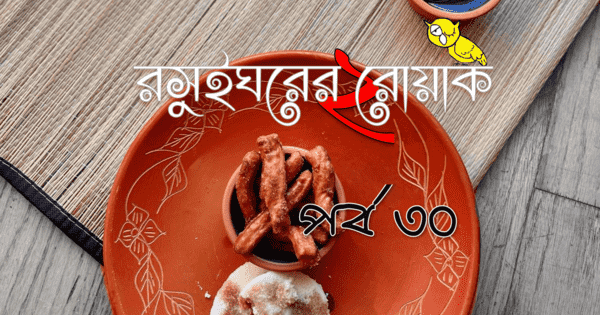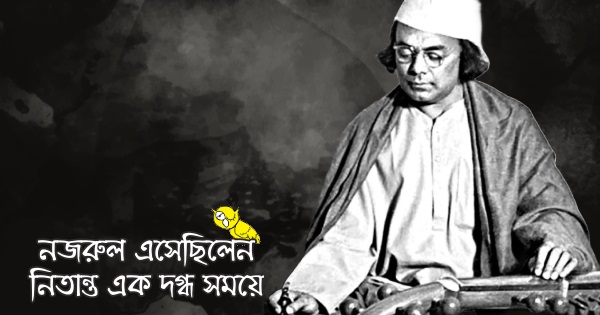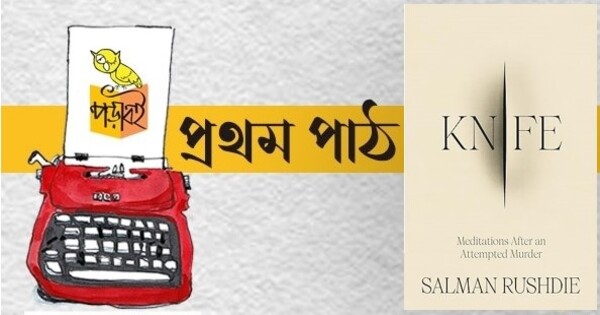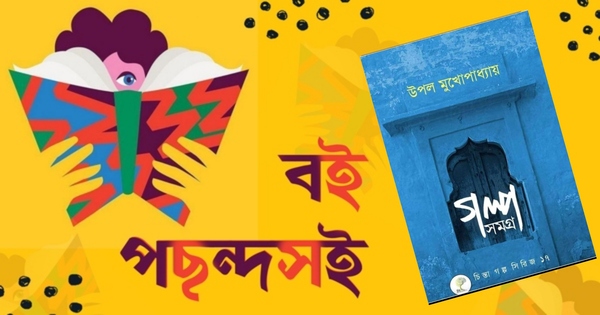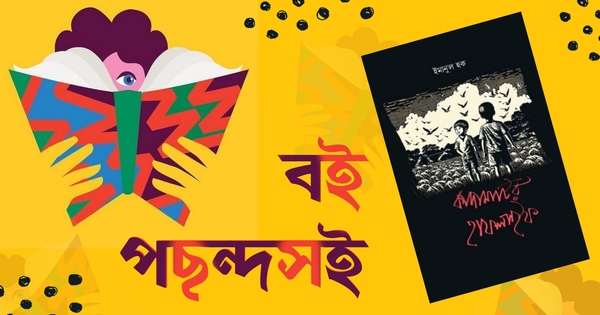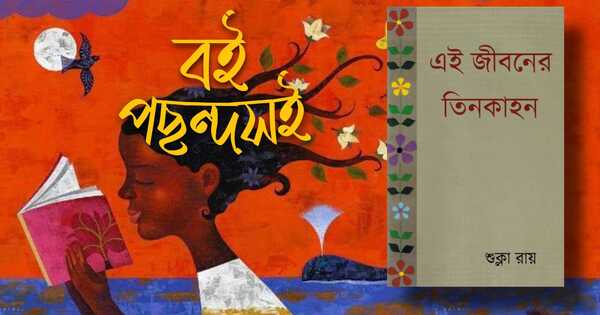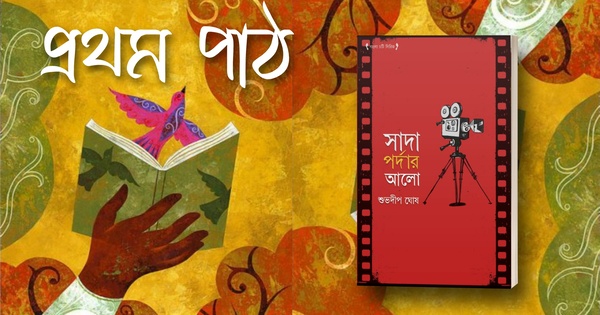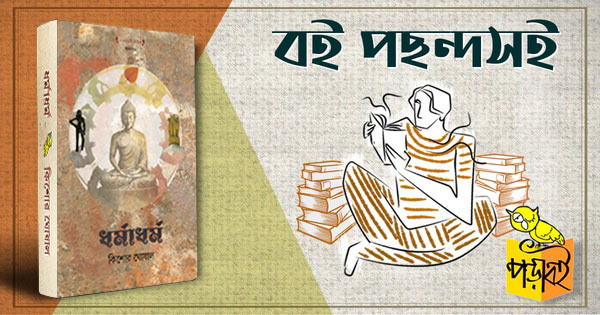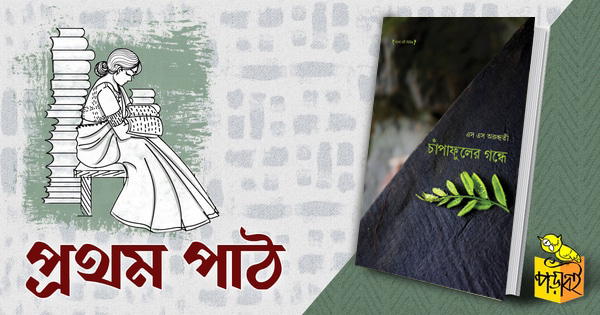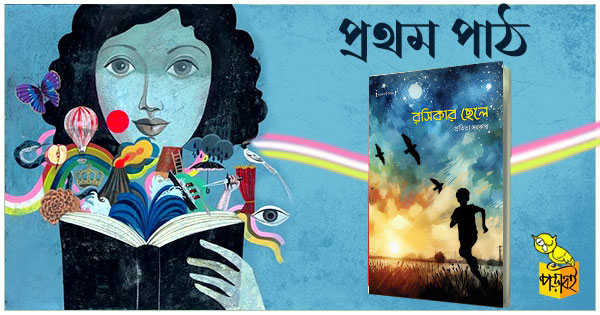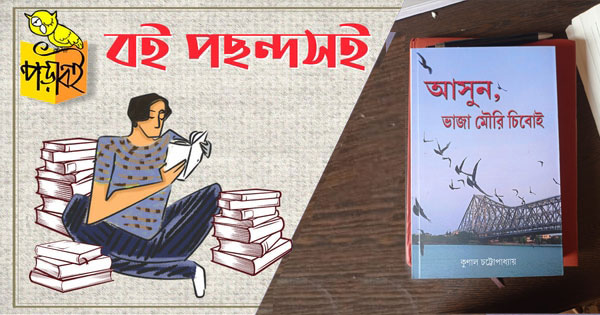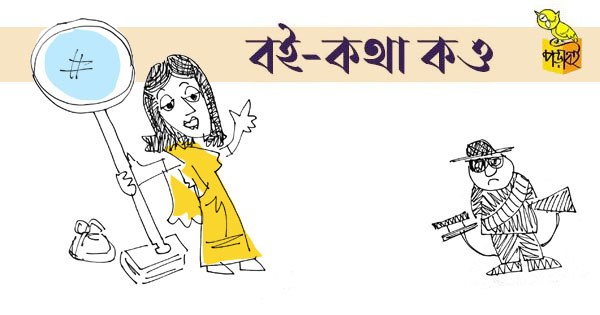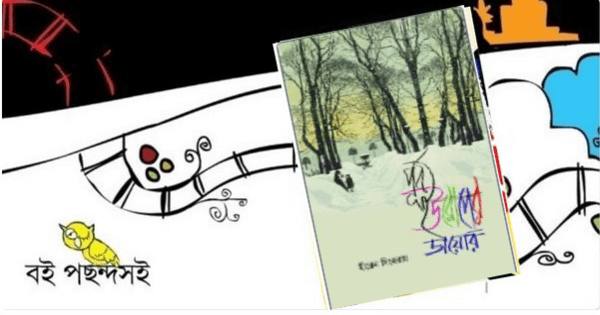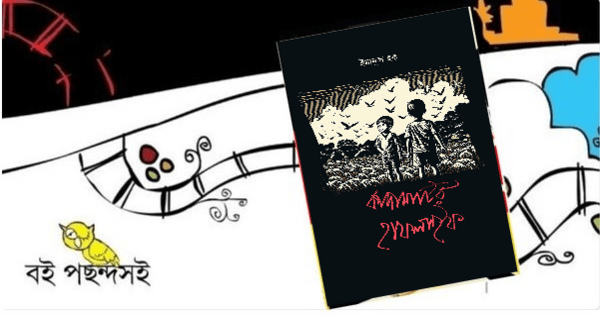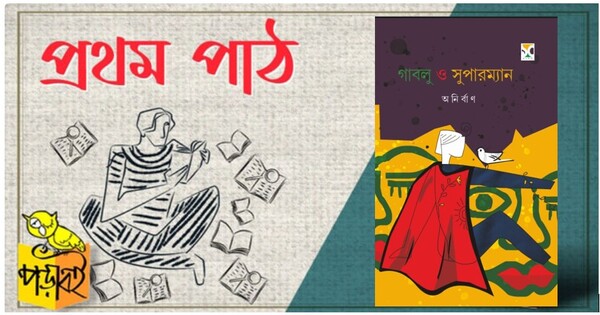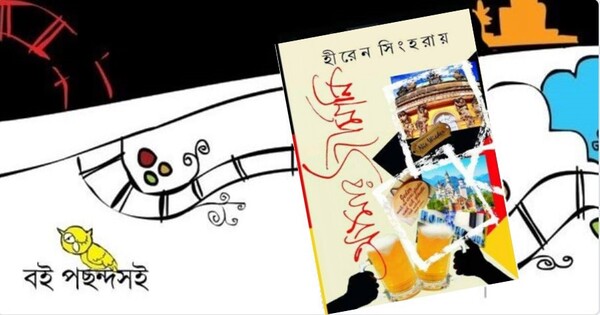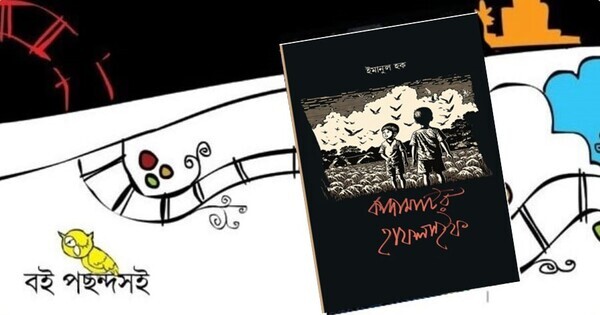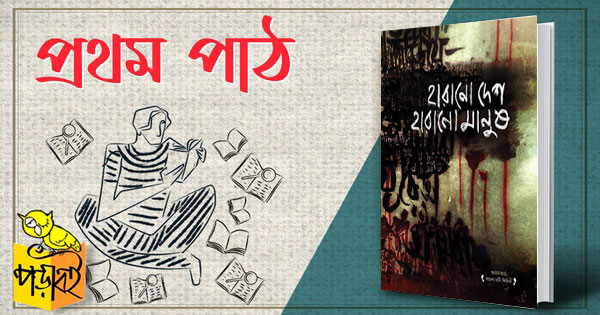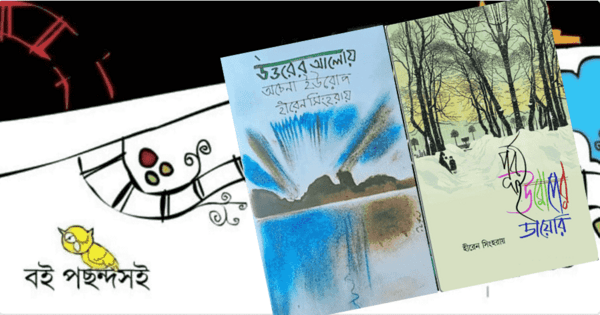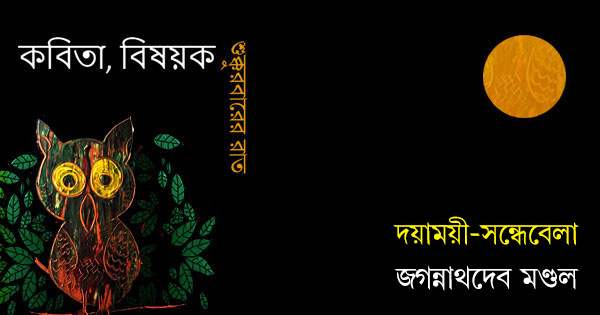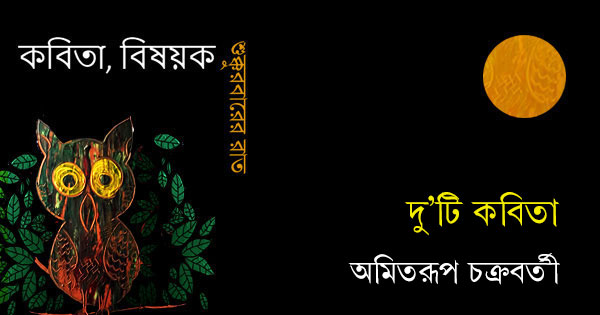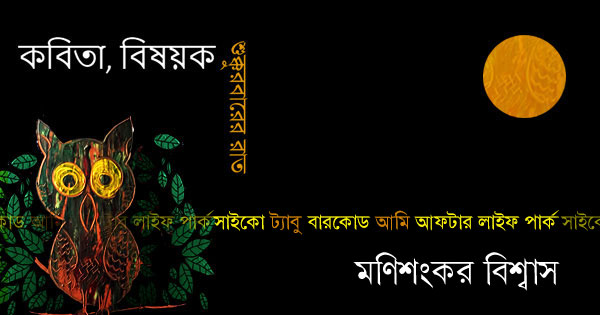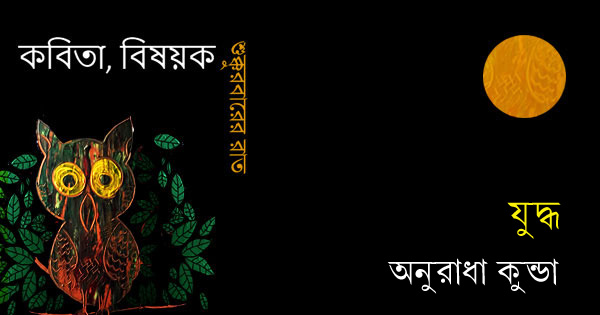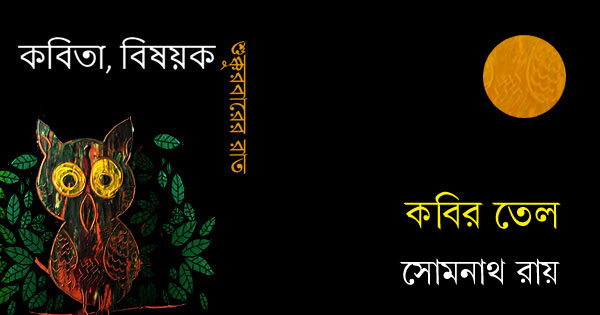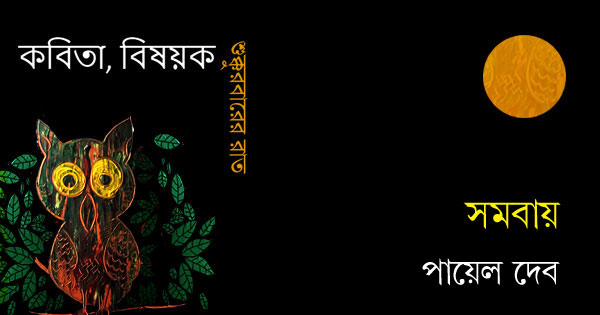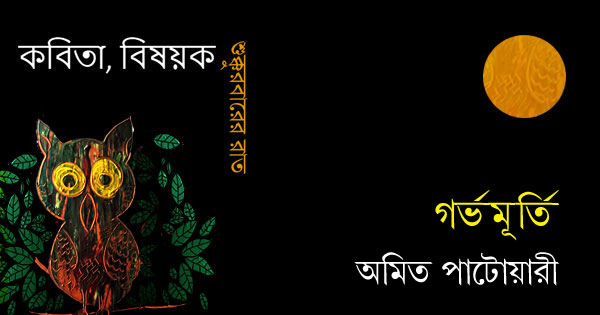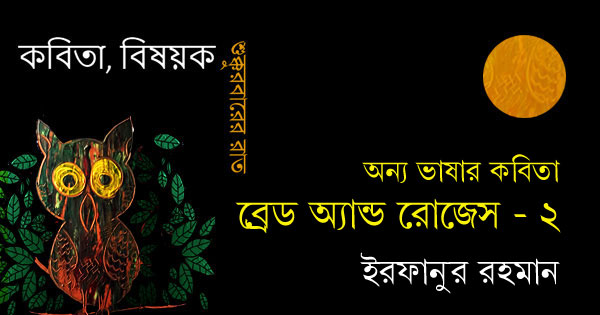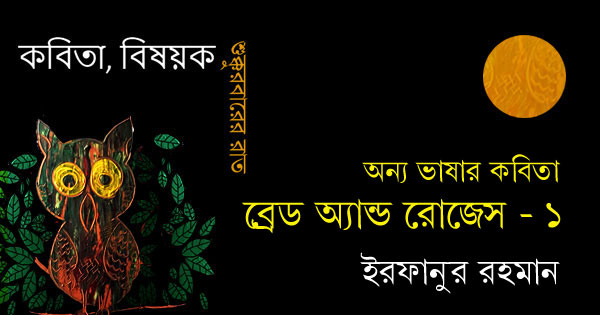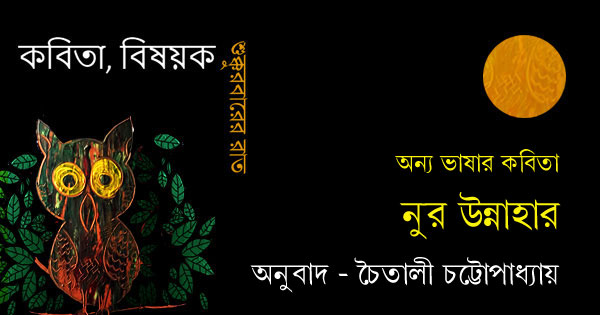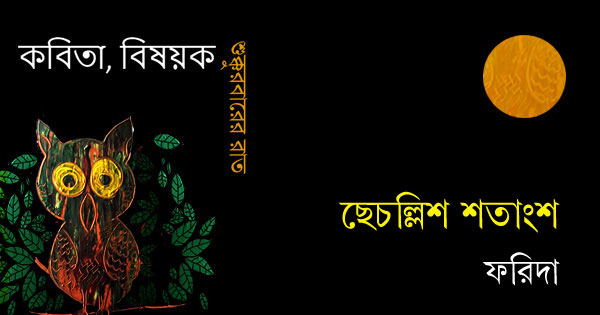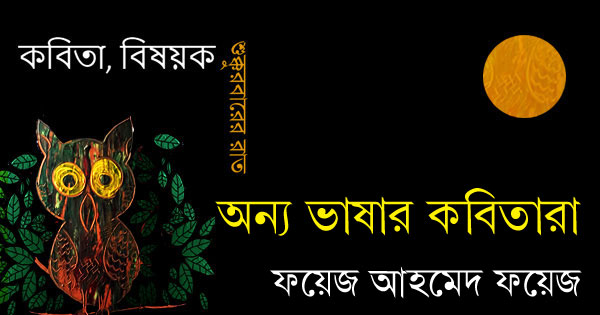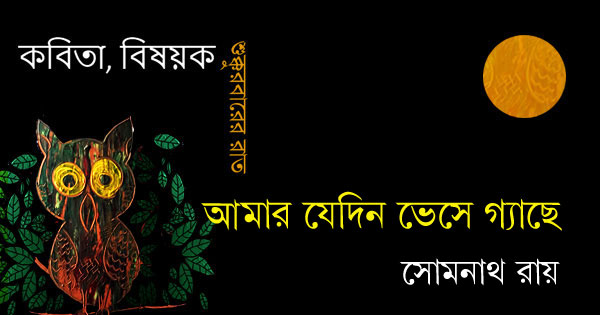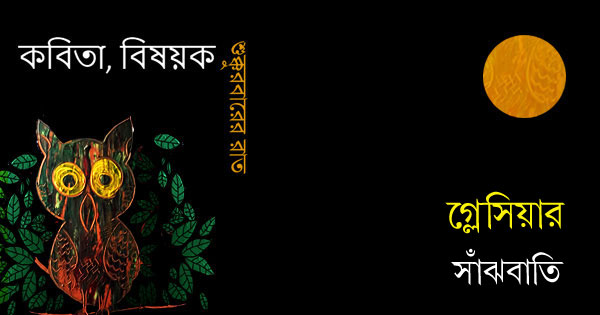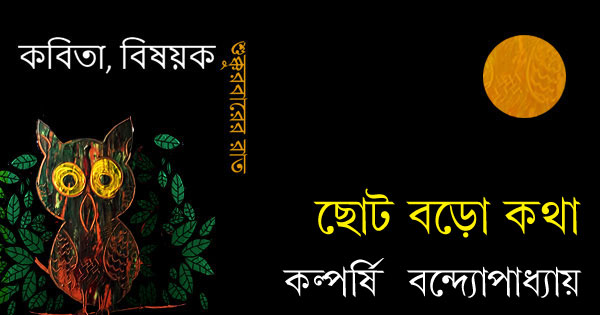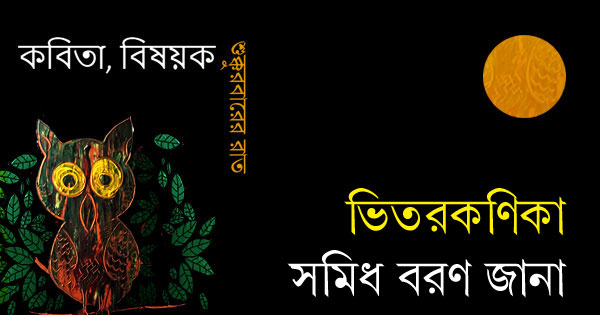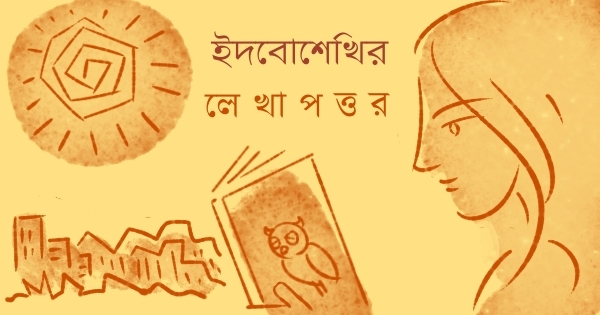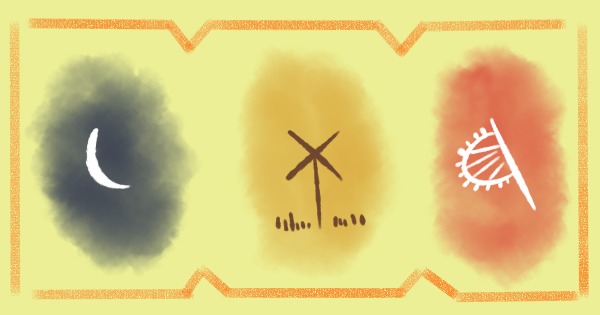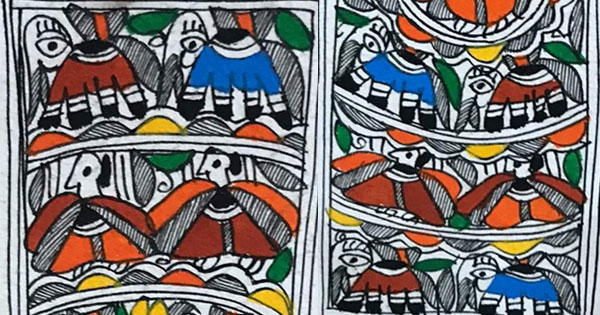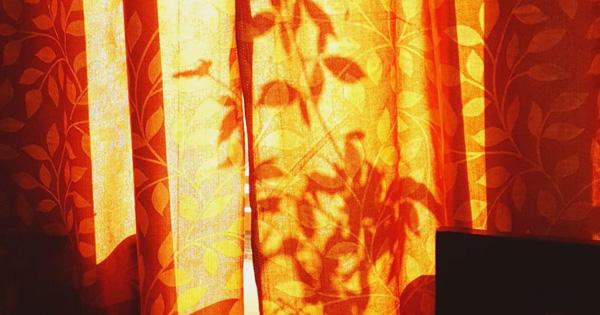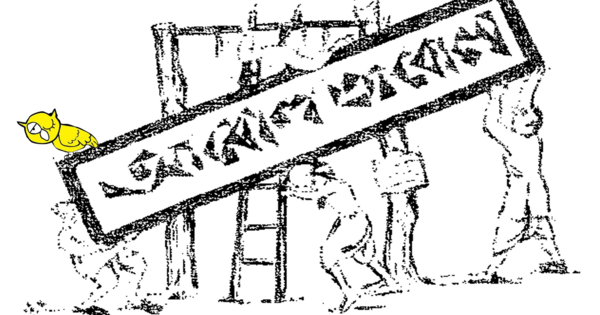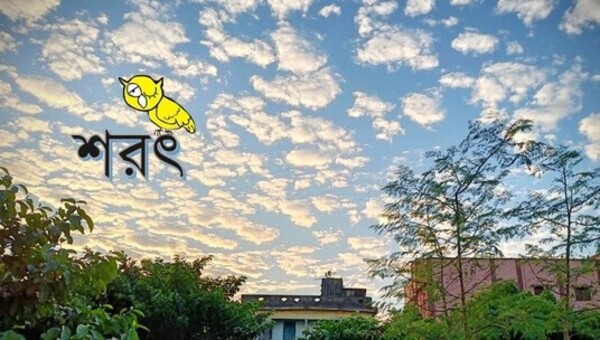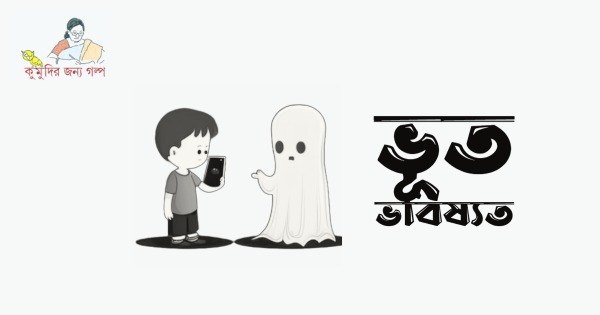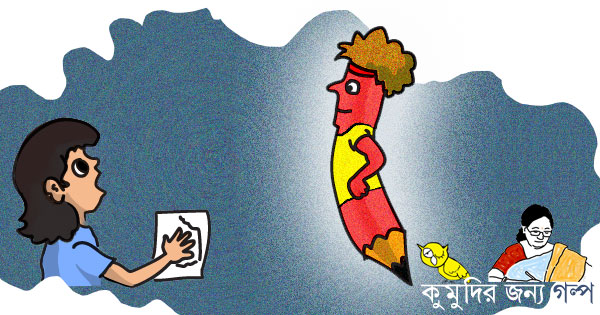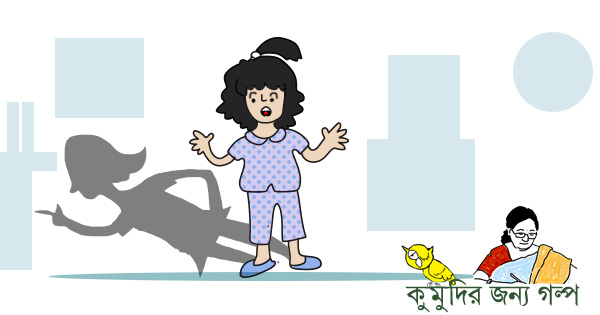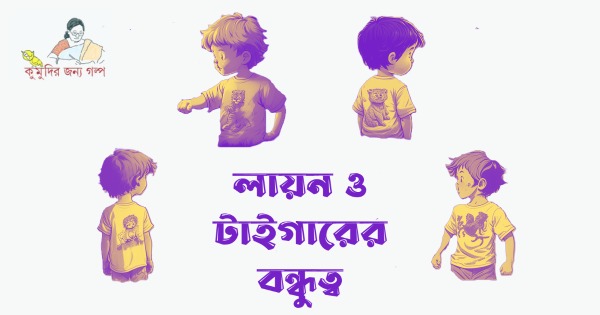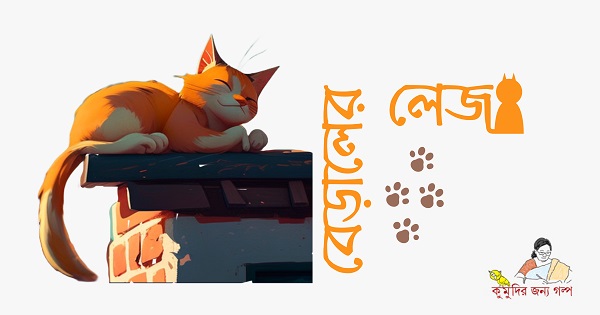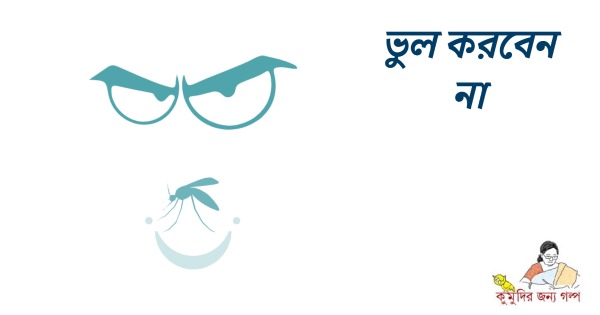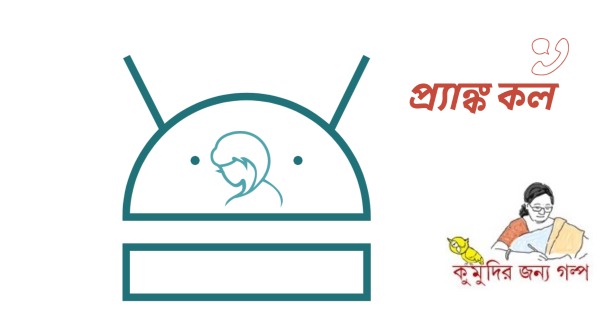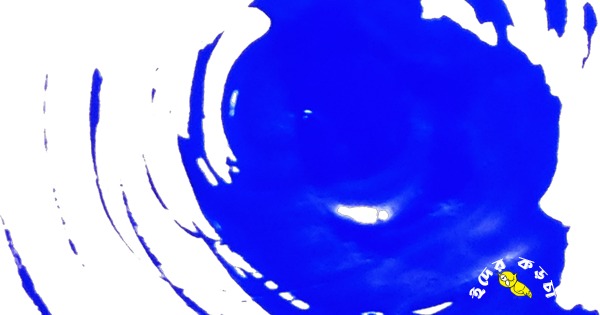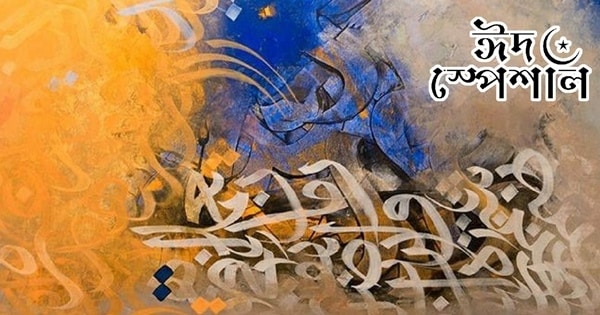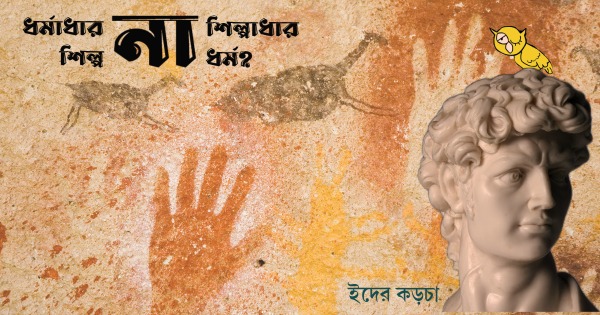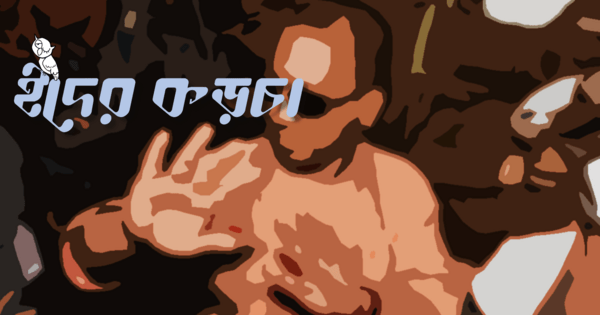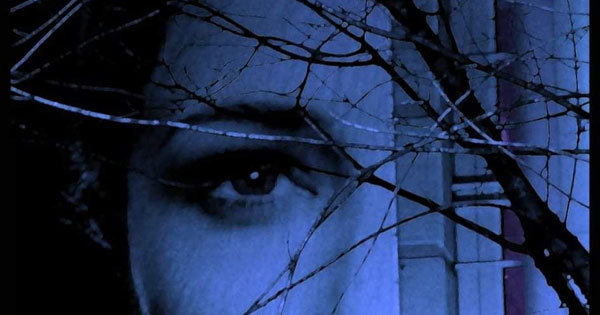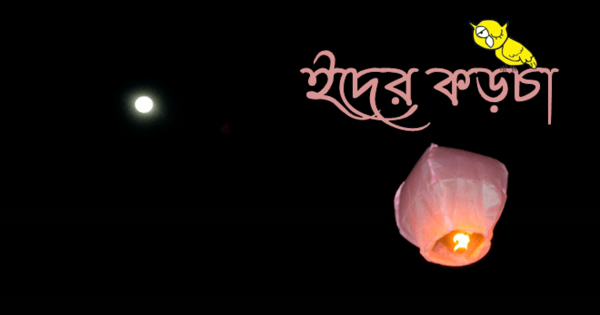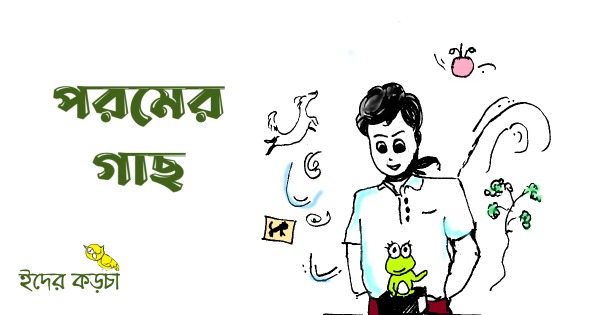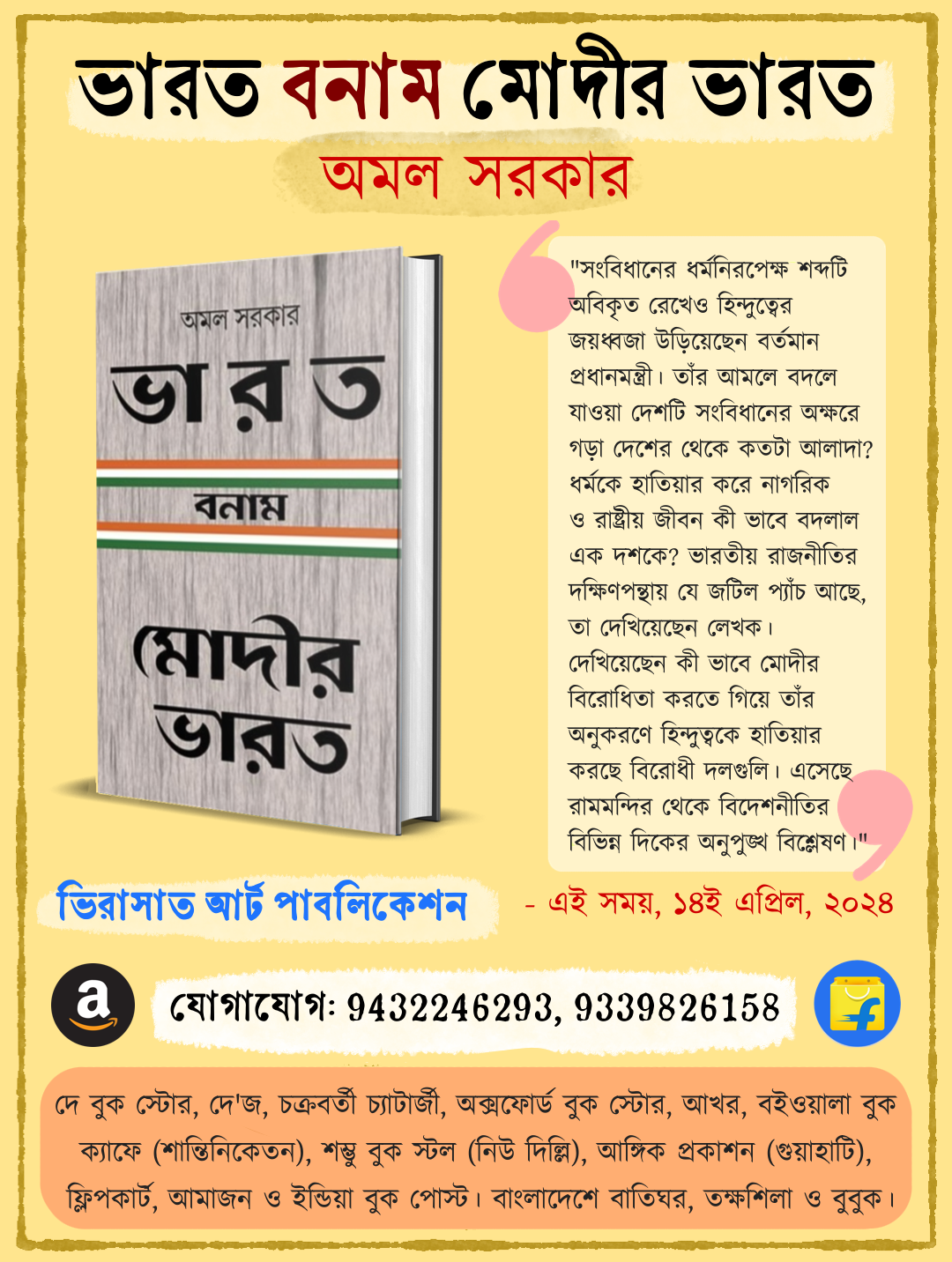তাজা বুলবুলভাজা...
মহারাজ ছনেন্দ্রনাথ ও বিদেশি চকলেটের বাক্স - রমিত চট্টোপাধ্যায় | অলংকরণ: রমিত চট্টোপাধ্যায়মহারাজ ছনেন্দ্রনাথ ওরফে ছেনু তখন থেকে অপেক্ষা করে রয়েছে কখন চিঠিটা সবার পড়া শেষ হবে। বাড়িতে কারুর চিঠি আসা মানেই ওর খুব মজা, আরেকটা ডাকটিকিট এসে খাতায় জমা হবে। খাতায় ডাকটিকিটটা সাঁটার কায়দাটা একটু খটোমটো। ওকে তেতলার দাদাই পুরোটা শিখিয়েছিল। প্রথমে খামের পিছনদিকটা অল্প জল দিয়ে ভিজিয়ে তারপর আলতো করে ব্লেড ঘষে ঘষে খুউব সাবধানে স্ট্যাম্পটা তুলে শুকিয়ে নিতে হবে। এরপর পাতলা একফালি সেলোফেন পেপার আধভাঁজ করে স্ট্যাম্পের পিছনে অল্প একটুকুনি আঠা লাগিয়ে সেলোফেন পেপারের আরেকটা দিক আলতো করে ধরে খাতায় চিপকে দিতে হবে। এই করে করে ছেনুর খাতায় এত্তোগুলো ডাকটিকিট জমে গেছে।আজকে সকালে তেতলার পিসিমার কাছে যে চিঠিটা এল, দাদা মানে পিসিমার ছেলে অনেকক্ষণ ধরে পিসিমাকে পড়ে পড়ে শোনাচ্ছে। ছেনু গিয়ে দু'বার দরজার সামনে থেকে ঘুরেও এল, কত লম্বা চিঠি রে বাবা! শেষে আর থাকতে না পেরে ছেনু গিয়ে পিসিমাকে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করেই ফেলল, কার চিঠি গো? দেখা গেল অদ্ভুত ব্যাপার, পিসিমা হাসছে, অথচ চোখের কোণে জল, পিসিমা হেসে বলল, কে আসছে জানিস? কান্টু আসছে রে কান্টু, তোর কান্টু দাদা। এদ্দিন পর ও আসছে, শুনে বিশ্বাসই করতে পারছি না, তাই তো বারবার করে শুনছি।ছেনু ছোট্ট থেকে পিসিমার কাছে কান্টুদার অনেক গল্প শুনেছে, কিন্তু কোনোদিন কান্টুদাকে চোখে দেখেনি আজ পর্যন্ত। অবশ্য দেখবেই বা কি করে, ছেনুর জন্মের আগেই তো পিসিমার বড় ছেলে কান্টুদা সেই সাত সমুদ্দুর তেরো নদী পার করে কি একটা দেশ আছে, কানাডা না কি নাম, সেইখানে চলে গিয়েছিল। সেই থেকে সেখানেই থাকে আর মাঝে মধ্যে চিঠি লিখে খবরাখবর জানায়। শুরুর দিকে বাংলায় লিখত বটে কিন্তু পরে কি জানি কেন শুধু ইংরেজিতেই চিঠি পাঠায়, তাই অন্যরা পিসিমাকে তর্জমা করে পড়ে পড়ে শোনায় কি লিখেছে।পিসিমার মুখেই ছেনু শুনেছে, কান্টুদার নাকি ছোটো থেকেই খুব বিদেশ যাওয়ার শখ, বড় হয়ে কলকাতার চাকরিতে মন টিঁকছিল না, কান্টুদা শেষমেশ ঠিক করল, না, আর কোলকাতায় না, খাস বিলেতেই যেতে হবে। যেমন কথা তেমনি কাজ, পরিবারের কিছু টাকার সাথে, নানা আত্মীয়স্বজনদের থেকে আরো কিছু টাকা ধার নিয়ে একসাথে জমিয়ে জাহাজে চেপে সোজা রওনা দিল বিলেতে। লন্ডনে নেমে নানা জায়গায় ঘুরে তেমন কিছু সুবিধা করতে না পেরে মুখ ভার করে বসেছিল, এমন সময় কার কাছে শুনেছে, নানা জায়গার লোক এসে নাকি লন্ডনে প্রচুর ভিড় হয়ে গেছে আর ওদিকে আরও দূরে কানাডায় নাকি প্রচুর কাজের লোকের দরকার। কান্টুদা শুনেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল, তাহলে এখানে বসে থেকে লাভ নেই, চলো কানাডা! আবার লন্ডন থেকে জাহাজে চেপে পাড়ি দিল আটলান্টিক মহাসাগর পেরিয়ে কানাডায়।সেখানে তো ভীষন ঠাণ্ডা, কান্টুদার সাথে গরম জামা বলতে একটাই কোট ছিল। যাই হোক রাস্তা থেকে আরেকটা ওভারকোট কেনার পর খোঁজখবর করে কম পয়সায় একটা বাড়িও ভাড়া করা হল। সেই কোট পরে কান্টুদা এদিক ওদিক কাজের খোঁজে যায়, কিন্তু যে সব কাজ জোটে সেসব মনে ধরে না পুরসভার চাকরির পাশাপাশি যাদবপুরের নাইট থেকে ইন্জিনিয়ারিং পাশ করা কান্টুদার। সারাদিনে খুব সামান্য কিছুই পেটে পড়ে, সারাদিন ঘুরে ক্লান্ত হয়ে রাত্রে ঘরে ফিরে ঘুমিয়ে পড়ে। নতুন দেশে গিয়ে তো কিছুই ঠাহর করতে পারছে না, খাবার দাবার খেতে, টুকিটাকি জিনিসপত্র কিনতেই জমা টাকা হুহু করে খরচ হয়ে যাচ্ছে! দেখতে দেখতে দুটো মাস কেটে গেল, প্রথম মাসের বাড়িভাড়া তো শুরুতেই দিয়ে দিয়েছিল, বাড়িওলা এবার এসে পরের মাসের ভাড়া চাইছে। কান্টুদা অনেক করে বোঝায়, ক'টা দিন দাঁড়াও, আমি চাকরি পেয়েই ভাড়া মিটিয়ে দেব। বুঝিয়ে সুঝিয়ে দিন দশেক কোনোক্রমে আটকে রাখা গেছিল, কিন্তু কপালের লেখা কে আটকাবে! একদিন খুব বৃষ্টি পড়ছে তার মধ্যে বাড়িওলা খুব চিৎকার চেঁচামেচি করে কান্টুদাকে বাক্সপ্যাঁটরা সমেত বাড়ি থেকে বের করে দিল। কান্টু দা কি আর করে, কোটখানা গায়ে চাপিয়ে বাক্স হাতে করে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে রাস্তায় অন্য একটা বাড়ির নীচে একটু আড়াল মতো পেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আড়াল পেলেও, এমন জোর বৃষ্টি শুরু হল যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাকভেজা ভিজে গেল।এমনি সময় হঠাৎ একটা মেয়ে পাশের বাড়ির জানলা থেকে মুখ বাড়িয়ে, কান্টুদাকে দেখতে পেয়ে বলল, ওখানে দাঁড়িয়ে আছো কেন? ভিজে যাবে তো! কে তুমি? কান্টুদা কি আর করে, মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, ইন্ডিয়া থেকে এসেছি চাকরি করতে, একটু বিপদে পড়েছি, বৃষ্টিটা ধরলেই চলে যাব।তাতে মেয়েটা বলে, ওখানে দাঁড়িয়ে থেকো না, বৃষ্টির মধ্যে ঠাণ্ডায় জমে যাবে, দরজা খুলে দিচ্ছি, ওপরে এসে বসো। তারপর গরম চা খেতে খেতে মেয়েটা কান্টুদার মুখ থেকে গোটা ঘটনা শুনল। নরম মনের মেয়ে, শুনে টুনে বলল, এটা আমার দিদার বাড়ি, আমি দিদার সঙ্গেই থাকি। তোমার তো থাকার কোনও জায়গা নেই, এক কাজ করো, যদ্দিন না চাকরি পাচ্ছো এখানে আমাদের সাথেই থাকো, আমি দিদার সাথে কথা বলছি। আপাতত জামাকাপড় বদলিয়ে শুকনো কিছু পরে নাও।পিসিমা যখন গল্পটা ছেনুকে বলেছিল, ছেনু তো শুনে অবাক, এতো দারুণ ব্যাপার! কান্টুদাকে আর ভিজতে হল না, আচ্ছা ওদিন যে অত করে সাহায্য করল, সেই মেয়েটা কে গো? পিসিমা বলেছিল, দাঁড়া দেখাচ্ছি, বলে কোন একটা ডায়েরির মধ্যে থেকে একটা টুকটকে ফর্সা গোলগাল মেয়ের ছবি বের করে ছেনুর হাতে দিয়ে বলল, এই দ্যাখ। ছেনু হাতে নিয়ে সেই মেমসাহেবের ছবি দেখে অবাক হয়ে বলল, সেই ছবি তুমি কী করে পেলে? পিসিমা বলে, ওমা পাবো না কেন? কান্টুই তো পাঠিয়েছে। ভালো করে দেখে রাখ, এই হল তোর বৌদি, জুলি বৌদি। ওখানে চাকরি বাকরি জুটিয়ে সেই জুলির সাথেই তো পরে ওর বিয়ে হয়েছে।তারপর অনেক দিন কেটে গেছে, কান্টুদা পাকাপাকিভাবে কানাডাতেই থাকে আর মাঝে মাঝে চিঠিতে খবরাখবর পাঠায়, তেমনই এক চিঠি আজ সকালে এসেছিল। তাতে কান্টুদা জানিয়েছে, সে জুলি বৌদি আর বাচ্ছাদের নিয়ে এবার কোলকাতায় আসছে সবার সাথে দেখা করতে। সেই কথা শুনে তো সারা বাড়িতে হইহই পড়ে গেল। বিদেশের অতিথি তার ওপরে আবার বাড়ির বউ! তার সামনে তো বাড়ির একটা প্রেস্টিজ আছে নাকি? সাথে সাথে রংমিস্তিরির কাছে খবর গেল, সারা বাড়ি চুনকাম করা হবে। তিন বোতল অ্যাসিড কিনে আনা হল, পুরো বাথরুম সেই দিয়ে পরিষ্কার করা হবে ঝকঝকে তকতকে করে। খাবার পরিবেশনের জন্য এল চকচকে নতুন কাঁসার থালা-বাটি-গ্লাস। আরও হ্যানো ত্যানো নানান নতুন নতুন জিনিস কেনার লিস্টি তৈরি হল। মোটকথা যেভাবেই হোক শেয়ালদার সম্মান যাতে বজায় থাকে সেই চেষ্টার কোনও ত্রুটি রাখা যাবে না।এই সব দৌড়াদৌড়ির মধ্যেই টুকটুক করে কান্টুদাদের আগমনের দিন এসে পড়ল। পিসেমশাই আর দাদা মিলে সেই দমদম এয়ারপোর্ট থেকে আনতে যাবে, সকাল থেকে তার প্রস্তুতি চলছে। ছেলের জন্য নানান রকম রান্না করা চলছে পিসেমশাযের চিন্তা কানাডার বৌমা প্রথম দেখায় প্রণাম করবে, হ্যান্ডশেক করার জন্য হাত বাড়িয়ে দেবে, নাকি আবার ওদেশের রীতি মেনে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরবে!তেতলার দাদা জামা প্যান্ট পরে রেডি, বাবাকে বোঝাচ্ছে, আরে দাদা তো আছে, তুমি ঘাবড়াচ্ছ কেন। ওদিকে আবার রান্নাঘর জুড়েও প্রস্তুতি তুঙ্গে। ছেলের জন্য নানান রকম রান্না করা চলছে, পঞ্চব্যঞ্জন দিয়ে আপ্যায়ন না করলে চলবে! ওদিকে আবার চিন্তা পাঁঠার মাংস তো ঠিক আছে কিন্তু কানাডার লোকে পাকা রুইয়ের কালিয়া, আলু পটলের ডালনা, উচ্ছে ভাজা, বেগুন ভাজা এসব ঠিকমতো খাবে তো? আসলে এগুলো কান্টুদার খুব প্রিয় পদ ছিল তো।বাড়ির নিচে দুটো ট্যাক্সির হর্ন শোনা যেতেই বাড়িজুড়ে যেন হাজার ওয়াটের বাল্ব জ্বলে উঠল। কেউ রান্নাঘরে ছুটছে, কেউ গ্লাসে করে জল নিয়ে আসছে আর বাকিরা সবাই মিলে সিঁড়ির দুধারে ভিড় করে দাঁড়িয়ে উঁকি ঝুঁকি মারছে। ছেনুও মনে মনে উত্তেজনায় ফুটছে, এতদিনের গপ্পের চরিত্রদের সাথে আজ দেখা হবে! ওরা সমস্ত বাক্স-প্যাঁটরা নিয়ে উঠতেই সটান বরণডালা হাতে পিসিমার মুখোমুখি। বিয়ে অনেকদিন হতে পারে, কিন্তু এবাড়িতে তো প্রথমবার, বরণ না করলে চলবে! সাথে চলল বাড়ির বাকি মহিলাদের সমবেত উলুধ্বনি।কিন্তু এদিকে মহারাজ ছনেন্দ্রনাথের মন ভেঙে গেছে, ছবির সাথে বাস্তবের বিন্দুমাত্র যে মিল নেই! ছবিতে যে গুবলু গাবলু মিষ্টি দেখতে বিদেশি মেয়েটাকে দেখেছিল, সে কই? এ তো বেশ রোগা, চোখ বসে গেছে, আর গরমের দেশে এসে ঘেমেনেয়ে একসা। সাথে আবার দুটো বাচ্চা ছেলেও আছে, ছেনুর থেকে বয়সে বোধহয় একটু ছোটই হবে কিন্তু দেখতে পুরোদস্তুর সাহেব। তারা কী যে বলছে ছেনু কিছুই বুঝতে পারছে না, তবে দেখল কান্টুদা কিছু একটা বলতেই টুক করে নিচু হয়ে পিসিমাকে প্রণাম করে ফেলল আর মুখে তাদের সারাক্ষণ হাসি লেগেই রয়েছে।বৌদিও ঢুকেই হাতজোড় করে সবাইকে নমস্কার করল, যা দেখে সবাই ইমপ্রেসড। প্রণাম টনামের পালা চুকিয়ে মালপত্র নিয়ে বাড়িতে ঢুকতে ঢুকতে পিছনে দেখা গেল বিশাল বিশাল দুটো সুটকেস নিয়ে দাদা আর পিসেমশাই আসছে, পিসেমশাইয়ের মুখটা বেশ হাসি হাসি। আবার তার পিছনে দেখা গেল ছেনুর বড়দাও চলে এসেছে কান্টুদাদের জন্য প্রচুর সন্দেশ, রসগোল্লা, জিলিপি, সিঙাড়া, চমচম বাক্সভর্তি করে নিয়ে। কখন যে টুক করে এসব আনতে চলে গিয়েছিল, ছেনু টেরই পায়নি।তা সেসব সাজিয়ে দেওয়া হল প্লেটে করে। পিসেমশাই আবার বকাবকি করছে বড়দাকে, এত বেশি মিষ্টি টিষ্টি আনার জন্য, পিসেমশাইয়ের ধারণা সিঙাড়া, জিলিপি, এসব আনা উচিৎই হয়নি, এসব আনহেলদি খাবার ওরা ছুঁয়েও দেখবে না। কিন্তু কি আশ্চর্য! ওই বাচ্চা দুটো প্লেটের সবকিছু নেড়েচেড়ে দেখে প্রথমে সিঙাড়াটা ভেঙেই মুখে দিল। নতুন রকমের খাবার খেয়ে মুখ খুশিতে আরো উজ্জ্বল হয়ে বলে উঠল, বলে, ভেরি ভেরি টেস্টি, আই লাইক ইট! তা শুনে বড়দার আনন্দ আর দেখে কে! কান্টুদা ও একটু নিশ্চিন্ত হলো ওদের ভালো লেগেছে দেখে। শেষমেশ দেখা গেল, এখানকার খাবার দাবার সবারই পছন্দ হয়েছে, সাথে চামচ দিয়ে জিলিপি আর সিঙাড়া খাওয়ার কায়দা দেখে বাড়ির লোকেরা একটু মুখ টিপে হেসেও নিল।জলখাবার পর্ব মিটতে ওদের খাটে নিয়ে গিয়ে বসানো হল একটু বিশ্রাম নেওয়ার জন্য, এতটা পথ জার্নি করে এসেছে। দুটো বাচ্চার নামও জানা গেল, পিটার আর ম্যাক্স। পদবি অবশ্য ব্যানার্জি। তো খাওয়া দাওয়ার পর পিটারের বড় বাইরে পেয়েছে, দাদা দেখিয়ে দিল বাথরুম- ওই যে বারান্দার শেষ প্রান্তে। যাক, এই মুহূর্তের জন্যই বাথরুম ভালো করে চুনকাম করিয়ে অ্যাসিড ঢেলে খুবসে পরিষ্কার করা হয়েছে, অবশ্য তাতেও একটা খিঁচ রয়েই গেছে। এই বাড়ির বাথরুমে তো আর ইউরোপিয়ান কমোড নেই, পা ভাঁজ করা দেশি প্যান, সেটায় বসতে পারবে কিনা চিন্তার বিষয়। তবে দেখা গেল বিশেষ বেগ মানুষকে প্যান আর কমোডের পার্থক্য নিয়ে মাথা ঘামাতে দেয় না, ও দিব্যি ভালো ছেলের মতো কাজকর্ম সেরে ভেতরে না পেয়ে, বাইরে মাথা বাড়িয়ে টয়লেট পেপার চাইছে। তারপর দাদা গিয়ে বোঝাল, টয়লেট পেপারের কোনো ব্যবস্থা নেই, জলেই ধুতে হবে। ছেনু দেখল সে পড়েছে ভারি মুশকিলে, অবশেষে কান্টুদা ভিতরে গিয়ে ব্যাপারটা সামাল দেয়। এখানকার কায়দা দেখে বাচ্ছাটা তো অবাক! তবে ভালো ভাবেই মানিয়ে নিয়েছে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে।এরমধ্যে পিসেমশাই গেলেন রান্নাঘরে ব্যস্ত পিসিমাকে ডাকতে, চলো চলো, রান্না তো হয়েই এসেছে প্রায়, এবার একটু ধাতস্থ হয়ে ছেলের সাথে বসে দুটো কথা বলো। একবার দেখো ছেলে কিরকম ফুল সায়েব হয়ে গেছে, চোস্ত ইংরেজিতে কথা বলছে, উফ্, শুনেও গর্ব হয়! পিসিমা হাতের কাজ সামলে ভীষণ উজ্জ্বল মুখ নিয়ে ঘরে গিয়ে বসলেন, কতো বড়ো হয়ে গেছিস রে, আসতে কষ্ট হয়নি তো?কান্টুদা বলে, নো নো নট অ্যাট অল। হাউ আর ইয়ু?শুনেই পিসিমা ভেবলে গেলেন, বলে কি? তারপর উনি যাই বলছেন কান্টুদা উত্তর দিচ্ছে ইংরেজিতে। আর পিসিমা আরো ঘাবড়ে যাচ্ছেন। শেষে পিসেমশাইকে হাঁক পাড়লেন, ওগো শুনছ, এসব কী বিড়বিড় করছে গো, ছেলে কি পাগল হয়ে গেল!অবস্থা বেগতিক দেখে কান্টুদা বলে উঠল, নো নো, আয়াম ফাইন। জাস্ট ফরগট হাউ টু টক ইন বেঙ্গলি, বাট আই আন্ডারস্ট্যান্ড ইয়োর ওয়ার্ডস পারফেক্টলি। পিসেমশাই তখন এসে পড়েছিলেন, পুরো ঘটনাটা পিসিমাকে বোঝাতে, পিসিমার চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়তে লাগল। ছেনু পাশ থেকে ব্যাপারটা পুরো দেখছিল, এতক্ষণ কান্টুদা কী যে বলছিল সেও একবর্ণ বুঝতে পারেনি, কিন্তু পিসিমাকে কাঁদতে দেখে আর থাকতে পারলনা। দাদাকে জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে গো, পিসিমা কাঁদছে কেন! কান্টু দাদা কি পিসিমাকে বকেছে? দাদা আর পিসেমশাই ইংরেজি ভালোই বুঝত। দাদাই গোটা ঘটনাটা ছেনুকে বুঝিয়ে বলল, কান্টুদা আর বাংলায় কথা বলতে পারছেনা বলে পিসিমা খুব দুঃখ পেয়েছে।ব্যাপারটা শুনেও ছেনুও মনে খুব কষ্ট পেল, ভাবল দূর দূর, বিদেশ থেকে এসছো তো কি হয়েছে, যাও কথাই বলবোনা তোমার সাথে।ঘরে এসে দেখে ছোড়দা কী একটা কাগজ খুলে পড়ছে, ছেনু বলে এই শোন না, কানাডা কত দূরে রে?- অনেক দূর এখান থেকে, আমাদের হলো এশিয়া, তার পাশে ইউরোপ, তারপর আটলান্টিক মহাসাগর পেরিয়ে উত্তর আমেরিকার মধ্যে হলো গিয়ে কানাডা।- আমেরিকা মানে ওই দেশটা, যেটার ওপর তোর রাগ?- না উত্তর আমেরিকা একটা মহাদেশ, তার মধ্যে একটা দেশ আমেরিকা, তার পাশেই কানাডা।- যেখানেই হোক গে, একদম যাবি না কানাডায়, একদম যাবি না।ছোড়দা যারপরনাই অবাক হয়ে বলে, কেন কী হয়েছে কানাডায় গেলে? আর আমি খামোখা কানাডা যেতেই বা যাবো কেন?ছেনু ঠোঁট উল্টে বলে, ওখানে গেলেই তো সবাই বাংলা ভুলে যায়, বিচ্ছিরি দেশ!তবে ছেনু বেশিক্ষণ রাগ করে থাকতে পারলো না, একটু পরেই বদ্দি আর ছোদ্দির ডাক পড়ল পিসিমার ঘরে। ছেনুও পিছু পিছু গিয়ে দেখে, সেই সুবিশাল সুটকেসের একটা খোলা হয়েছে আর তার পেটের ভেতর কত্তো জিনিস। বদ্দি আর ছোদ্দির জন্য নকশাকাটা রঙিন কাঁচের শিশিতে করে কি একটা এনেছে। শিশির ওপরে একটু চাপ দিতে কি সুন্দর একটা গন্ধ বেরোলো। জিনিসটার নাম নাকি অডিকোলন, দুজনেই তো পেয়ে খুব খুশি (পরে একবার ওই শিশি কি ভেবে মা মাথাব্যথার ওষুধ হিসেবে মাথায় লাগাতে গিয়েছিল, মাঝে মধ্যে টুকটাক রাগ করলেও, বদ্দিকে ওইদিনের মতো অমন রেগে যেতে ছেনু কক্ষনো দেখেনি)। ছেনু সব বাইরে থেকেই দেখছিল। যদিও অন্য সময় পিসিমাদের ঘরে ছেনুর অবাধ যাতায়াত থাকে, তবে এখন তো ওকে ডাকেনি, কাছে যাবে কেন! মানসম্মান বলেও তো একটা জিনিস আছে না কি, মহারাজ বলে কথা। তবে ও বুঝতে পারল ওর কপালেও একটা দারুণ বিদেশি উপহার নাচছে। কারণ এ বাড়িতে তাকেই সবাই সবচে ভালোবাসে, দিদিদেরকে যদি এত সুন্দর জিনিস দেয়, তবে ওকে না জানি কি দেবে, ভেবেই ওর পেটের মধ্যে বুড়বুড়ি কেটে উঠল।ওই তো সুটকেস থেকে কি সুন্দর একটা জামা বের করছে, তবে বেশ বড়ই হবে ওর গায়ে। ওঃ, ওটা এনেছে কান্টুদার ভাইয়ের জন্য। এরপর বেরোল আর একটা কাঁচের বোতল , ওটা পিসিমার জন্য, পিসিমা সুগন্ধি খুব ভালোবাসে কিনা। এরপর একে একে বার হতে থাকল ছাতা, কলম, ব্যাগ, আরও কত কি। এক একটা জিনিস এক এক জনের জন্য। তারপর বেরিয়ে এল একটা বড়ো রঙচঙে টিনের গোলমতো বাক্স। ওমা! বাক্সটা কি সুন্দর দেখতে। একটা বরফের পাহাড়ের সামনে চকোলেটের ছবি। তাহলে এটা নিশ্চই বিদেশি চকলেটের বাক্স। যাক, এটাই তাহলে ছেনুর জন্য এনেছে। সত্যি কান্টুদার পছন্দের তারিফ না করে ছেনু পারে না। ওকি! বাক্সটা পিসেমশাইকে দিয়ে দিল কেন? আচ্ছা রাখতে দিল বোধহয়, পরে ওকে ডেকে দিয়ে দেবে, থাক যখন ডাকবে তখন আসবো, এখন আর দাঁড়িয়ে কাজ নেই।দুপুরে যখন কান্টুদারা খেতে বসল, সেও যেন এক দর্শনীয় বিষয়। সবাই দূরে দাঁড়িয়ে গোল হয়ে দেখছে। বেগুন ভাজা, পটল ভাজা, আলু ভাজা এসব খুবই পছন্দ হয়েছে বাচ্চাদের। সবকিছুই 'ডেলিশিয়াস' বলে হাসি মুখে খাচ্ছে চামচ দিয়ে। কান্টুদা হাত দিয়েই খাচ্ছে আর এটা ওটা করে ওদের খেতে সাহায্য করছে। জুলিবৌদি কান্টুদাকে ফিসফিস করে কি একটা জিজ্ঞেস করল, সম্মতি পেয়ে মাথা নেড়ে নিজেও হাত দিয়েই খাওয়া শুরু করল। পটলের ডালনা শুধু শুধু খেতে যাচ্ছিল, ডালটাও, কান্টুদা ভাতে মেখে খাওয়া দেখিয়ে দিল। মুশকিল হলো মাছের কালিয়া নিয়ে। বড় বড় পেটির মাছই দেওয়া হয়েছে কিন্তু না বুঝে বোনলেস ভেবে কামড় বসাতেই বিপত্তি। ঘটনা বুঝতে পেরে পিসিমা জলদি এসে কাঁটা গুলো টেনে বের করে দিলে, সবাই তৃপ্তি করে খেতে পারল। নতুন স্বাদের খাবার পেয়ে সবাই খুব খুশি, জুলিবৌদিও হেসে বলল, রিয়েলি আমেজিং ফুড। তা আবার পিসিমাকে রিলে করা হতে পিসিমার মুখে অবশেষে একটু হাসির রেখা দেখা গেল।এরপর আবার পাঁঠার মাংস খেয়ে সবারই পেট দমসম। কান্টুদা ছাড়া কেউ আর চাটনি খেতেই পারলো না। খাবার নিয়ে পিটার আর ম্যাক্সের আনন্দ দেখে পিসিমা পিসেমশাইকে শুনিয়েই দিলেন, কি গো তবে যে বলছিলে বাঙালি খাবার ওরা নাকি খেতে পারবে না!খাওয়া দাওয়ার পর পিসেমশাই বললেন, দাঁড়া বালিশ টালিশ সব পেতে বিছানা করে দিই, তোরা একটু গড়িয়ে নে। কান্টুদা শুনেই বলে, আরে না না, আমি হোটেল বুক করেছি তো! আসলে ওরা এখানে এডজাস্ট করতে পারবে কিনা ভেবে আগে থেকেই হিন্দুস্তান ইন্টারন্যাশনালে রুম বুক করে রেখেছি। আর এইটুকু জায়গায় এতজন আঁটবেও না।অবশ্য পিসেমশাই এর মনের মেঘ আবার কেটে গেল পরদিন যেই ওরা আবার হই হই করে হাজির। আজ পিটার আর ম্যাক্স এর দাবি বাড়িটা তাদের ভালো করে ঘুরে দেখাতে হবে, এই বাড়িটা নাকি তাদের ভারি পছন্দ হয়েছে। তাদের কথায়, ভেরি নাইস হাউস, লাইক অ্যান ওল্ড ম্যানসন, ফিলস ভেরি চার্মিং। কান্টুদার ভাইই আজ গাইড, ওর পিছন পিছন পিটার আর ম্যাক্স লাফাতে লাফাতে চলেছে। কান্টুদার সুটকেস থেকে আজকে আবার একটা দারুণ জিনিস বেরিয়েছে - একটা ঝকঝকে ইয়াশিকা ক্যামেরা। ব্যাগের মধ্যে থেকে লেন্স বের করে তাতে এঁটে, ফিল্মের কৌটো থেকে ফিল্ম বের করে পরালো। সেই ক্যামেরা চোখে লাগিয়ে এদিক ওদিক খচ খচ করে ছবি তুলছে আর মাঝে মাঝে জুলিবৌদিকে সব স্থান মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করছে। সাথে ছোড়দাকে নিয়ে ছেনুও তাদের পিছু ধরেছে, আরে হাজার হোক নিজের রাজত্বে বেড়াতে আসা বিদেশি অতিথিদের প্রতি মহারাজেরও তো একটা দায়িত্ব আছে নাকি! ছাদে গিয়ে তো ওরা ভীষণ আনন্দিত। দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে, ওপর থেকে নিচের সবকিছু খুদে খুদে দেখাচ্ছে, দারুণ হাওয়াও দিচ্ছে। এমনকি তখন সেই ছাদের থেকে হাওড়া ব্রিজ পর্যন্ত দিব্যি দেখা যেত। ছাদেও কান্টুদা অনেক ছবি টবি তুলল। ছেনুর মনে হলো আহা, পিটার, ম্যাক্স আর জুলি বৌদির সাথে দাঁড় করিয়ে ওর ছবিও যদি একটা তুলত!তবে মহারাজ ছনেন্দ্রনাথ সবচেয়ে বেশি দুঃখ পেলেন যখন দেখলেন, তাঁর জন্যই উপহার হিসেবে নিয়ে আসা বিদেশি চকলেট বাক্স থেকে বের করে পিটার, ম্যাক্স আর পিসেমশাই দিব্যি আনন্দ করে খাচ্ছে। সোনালি রাংতা দেওয়া কি সুন্দর দেখতে গোল গোল চকলেটগুলো! সে দৃশ্য দেখে তিনি নিজেকে সান্তনা দিলেন, আসলে চকলেটগুলো শুধু তাঁর জন্য নয়, সবার খাওয়ার জন্যই আনা হয়েছে, ঠিকই তো, ভালো জিনিস সবাইকে দিয়ে থুয়েই খেতে হয়। পরে যখন পিসিমা ডেকে হাতে দেবে, তখনই খাওয়া যাবে না হয়।কান্টুদারা মোট দিনদশেকের মতো ছিল কোলকাতায়। তারই মধ্যে ঠিক হল, ওরা নাকি দার্জিলিং ঘুরতে যাবে। একবার এতদিন পর ভারতে আসা হয়েছে, কলকাতার বাইরেও দু একটা জায়গা একটু ঘুরে দেখে নেওয়াই ভালো। শুনে ছেনুর ভারি মনখারাপ হয়ে গেল, সবে দুজনার সঙ্গে বন্ধুত্ব হবে হবে করছিল, তার মধ্যেই আবার ঘুরতে চলে যাবে। পাঁচ দিনের মধ্যেই অবশ্য ওরা আবার ঘুরেটুরে ফেরত আসতে বাড়িটা আবার হইচইয়ে ভরে উঠল। আর দুদিন পরেই কানাডায় ফিরে যাবে।কান্টুদাদের চলে যাওয়ার দিন তেতলার দাদা ছেনুকে ডাকতে এলো, যাবি নাকি প্লেন দেখতে? ছেনু তো শুনেই একলাফে রাজি। ছোড়দাকেও ডাকতে, ছোড়দা বললো আজ কলেজ আছে হবে না। যাই হোক, ছেনু মাকে বলে, একটা ভালো দেখে জামা পরে, পিসেমশাই আর দাদার সাথে রওনা দিল হিন্দুস্তান ইন্টারন্যাশনাল হোটেলে, দার্জিলিং থেকে ফিরে কান্টুদারা আবার ওখানেই উঠেছে, রাত্রে হোটেলে থাকত, আবার সকাল সকাল চান টান করে শেয়ালদায় চলে আসতো। হোটেলের লবি দিয়ে চারিদিকে তাকাতে তাকাতে ছেনু লিফটে চড়ে ওদের ঘরের দিকে গেল। ঘরে ঢুকে দেখে ওরাও বেরোনোর জন্য তৈরি। সুটকেস টুটকেস হাতে নেওয়ার পর জুলিবৌদি পিটার আর ম্যাক্সের দিকে একবার তাকাতেই তারা তড়াক করে উঠে খাটের তলা, বাথরুম, আলমারি, টেবিলের ড্রয়ার কোথাও কিছু জিনিসপত্র পড়ে আছে কিনা সব খুঁজে দেখে ফেলল। ছেনু তো কাণ্ড দেখে তাজ্জব।যাই হোক হোটেল থেকে দুটো ট্যাক্সিতে চেপে ওরা সবাই দমদম এয়ারপোর্টে পৌঁছে গেল ঠিক সময়ে। ব্যাগপত্র চেকিং টেকিংয়ের পর এবার বিদায়ের পালা। ক'দিনেরই বা দেখা, তবুও ছেনুর গলায় যেন একটা মনখারাপ দানা বাঁধছিল। ওরা একসময় শেষবারের মতো হাতটাত নেড়ে ঘেরাটোপের মধ্যে হারিয়ে গেল। পিটার আর ম্যাক্সও অনেকক্ষণ ধরে হাত নাড়ছিল ওদের দিকে ফিরে ফিরে, মানে যতক্ষণ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল আর কি। ওরা চলে যেতে দুঃখ কাটাতে পিসেমশাই দুজনকে নিয়ে গেলেন প্লেনের নামা ওঠা দেখাতে। তখন টিকিট কেটে একটা ঘেরা বারান্দা মতো জায়গায় দাঁড়িয়ে প্লেন দেখা যেত। ছেনু তো সার দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা প্লেনগুলো দেখে পুরো হাঁ। অবাক হয়ে দেখছে কত বড় বড় সব ডানাওলা বাস। জানলাগুলো সব এই পুঁচকে পুঁচকে লাগছে। ছেনু ভাবে এগুলো সব আকাশে ওড়ে কী করে? এতে চেপেই তো কান্টুদারা এসেছে! ওমনি দাদা আঙুল দিয়ে দেখাল দূউউরে একটা প্লেন মাঠের মধ্যে দৌড় লাগিয়েছে। যত এগোচ্ছে দৌড়ের বেগ বাড়ছে। এক সময় সামনের চাকাটা টুপ করে মাটি ছেড়ে আকাশে উঠে পড়ল।বাড়ি ফিরেও ছেনু ওদের কথাই ভাবছিল। এক সময় আর থাকতে না পেরে তেতলায় পিসিমার ঘরের দিকেই পা বাড়াল। গিয়ে দেখে পিসিমা কি সব সেলাই টেলাই করছে, সব ছুঁচ সুতো বের করেছে। পিসিমা ওকে দেখেই হেসে বললো কেমন প্লেন দেখলে বলো? ছেনু মাথা নাড়তেই পিসিমা বললো ওখানে একটা বাক্স রাখা আছে, আনো তো দেখি একবার। ছেনু তাকিয়ে দেখে সেই বিদেশি চকলেটের বাক্স। দৌড়ে গিয়ে তাক থেকে সেটা পিসিমার কাছে নিয়ে আসতে আসতেই ওর মনে একটা খটকা লাগল, এত হালকা কেন? তবে কি মাত্র অল্প ক'টা পড়ে আছে আর!পিসিমা বললো এনেছ, দাও তো। পিসিমা বাক্সটা খুলতেই ছেনু দেখে চকলেটের কোথায় কি, বাক্স বেবাক ফাঁকা! পিসিমা ছেনুকে বললো খেয়েছিলে তো চকলেট? কেমন লাগল? ছেনু বলে, কই না তো!- সে কি পিসেমশাই দেয়নি? আসলে চকলেট ভালোবাসে বলে বাবার জন্য এই চকলেটের বাক্সটা এনেছিল কান্টু। পিসেমশাই শুরুর থেকেই এমন টপাটপ খাচ্ছে, আমি বললাম দিও কিন্তু সবাইকে। তারপর খোকনও ওর বন্ধুদের কয়েকটা দিয়েছে। তারপর যে ক'টা পড়েছিল ওরা দার্জিলিং যাওয়ার সময় আমি সঙ্গে করে পাঠিয়ে দিলাম। ইসসস্ মাঝখানে যে তুমি বাকি পড়ে গেছ, এই দৌড়াদৌড়ির মধ্যে আমি খেয়ালও করিনি। তারপর বাক্সটা ধুয়েমুছে সরিয়ে রেখেছিলাম ছুঁচসুতো রাখব বলে।ততক্ষণে মহারাজ ছনেন্দ্রনাথ আর ওখানে থাকলে তবে তো! তিনি চোখের জল মুছতে মুছতে দোতলায় দৌড় মেরেছেন।পুনশ্চ: দুদিন পর আবিষ্কার হলো, কান্টুদা সেই দারুণ ইয়াশিকা ক্যামেরাখানা ভুলে এই বাড়িতেই ফেলে চলে গেছে। দার্জিলিং থেকে ফিরে রিল বদলাবে বলে বোধহয় সরিয়ে রেখেছিল, আর বের করা হয়নি। বাড়িতে ফটোগ্রাফি একমাত্র ছেনুর বড়দাই ভালো জানতো। তাই পিসেমশাই আর কি করবেন ভেবে না পেয়ে, সেই ক্যামেরা বড়দাকেই দিয়ে দিলেন। বড়দার হাত বেয়ে কালক্রমে সেই ক্যামেরাখানা বহুদিন পর মহারাজ ছনেন্দ্রনাথের হস্তগত হয় ও তা দিয়েই পরবর্তীকালে তিনি দেদার ছবিছাবা তোলেন। মহারাজের সিন্দুকেরই কোনো এক কোণে সেই প্রাচীন ক্যামেরা, লেন্স টেন্স সমেত আজও বহাল তবিয়তে বিদ্যমান। তা বিদেশি চকলেটের বদলে বিদেশি ক্যামেরা - এই বা মন্দ কি!বিপ্লবের আগুন - পর্ব নয় - কিশোর ঘোষাল | ছবি: রমিত চট্টোপাধ্যায়৯ওরা চলে যেতে ভল্লা গ্রামের দক্ষিণ দিকে হাঁটতে শুরু করল। গ্রামের এদিকটা এখনও তার দেখা হয়নি। এদিকে বসত কম। বিচ্ছিন্ন কিছু আবাদি জমি, আর অধিকাংশই অনাবাদি পোড়ো জমি। ভল্লা হাঁটতে লাগল। অনেকক্ষণ চলার পর তার মনে হল, সে গ্রামের সীমা ছাড়িয়ে এসেছে। জনহীন প্রান্তর - কিছু বড় গাছপালা, ছোটছোট ঝোপঝাড় সর্বত্র। আরও কিছুটা গিয়ে তার কানে এল বহতা জলের শব্দ। অবাক হল – এমন রুক্ষ প্রান্তরে কোথা থেকে আসছে এই ক্ষীণ জলধ্বনি। এগোতে এগোতে ভল্লা ছোট্ট একটা নালার পাশে দাঁড়াল। পূব থেকে পশ্চিমে বয়ে চলেছে জলধারা। খুবই সামান্য – কিন্তু ভল্লার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কোথা থেকে আসছে, এই জলধারা? এ অঞ্চলে বর্ষা হয় সামান্যই – তাহলে কোন উৎসমুখ এই জলধারাকে সজীব রেখেছে এই মধ্য শীতেও। এই গ্রামের অবস্থান চিত্রটি সে মনে মনে চিন্তা করল কিছুক্ষণ। এই গ্রামে আসার সময় পাহাড়ের কোলে রাজপথের ধারে সেই সরোবর দেখেছিল। সেই রাজপথ থেকে অনেকটাই নিচে এই গ্রামের অবস্থান। আজ সকালে যে দীঘির ঘাটে সে বসেছিল, সেটি এই গ্রামের পূর্ব সীমানায় এবং তার পরেই রয়েছে খাড়া অনুচ্চ যে পাহাড়টি – তারই শীর্ষে রয়েছে রাজপথের সরোবরটি। আজ সকালে গ্রাম পরিক্রমণের সময় আরও কয়েকটি পুকুর সে লক্ষ্য করেছে। তাহলে ওই দুই সরোবর, ওই পুকুরগুলি এবং এই নালার উৎস কি একই? প্রকৃতির কি আশ্চর্য লীলা – সরোবর কিংবা পুকুরগুলি কখনো প্লাবিত হয় না, কিংবা জলহীনও হয় না। ওগুলিকে সম্বৎসর পরিপূর্ণ রেখে উদ্বৃত্ত জলরাশি প্রবাহিত হয় এই নালাপথে! বর্ষায় হয়তো এই নালার প্রবাহ গতি পায়। ভল্লা আশ্চর্য হল। সে নালাপথের উজান বরাবর এগিয়ে চলল পূর্বদিকে। লক্ষ্য করতে করতে চলল নালার এপাশের জমির প্রকৃতি, গাছপালা ঝোপঝাড়। ভল্লার কৃষিকাজে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই। তবু রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে যেটুকু সে দেখেছে, তার মনে হল, আপাত অনুর্বর এই জমিকেও কৃষিযোগ্য করে তোলা সম্ভব। একটু পরিশ্রম করলে, এই নালার জল কৃষিকাজে সম্বৎসর ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রায় ক্রোশার্ধ হেঁটে সে পৌঁছল গ্রামের পূর্বসীমানার সেই পাহাড়তলিতে। এই জায়গাতেই পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসা একটি শীর্ণ জলধারা সমতলে নেমেছে। এই জায়গায় জলধারা কিছুটা বিস্তৃত, বড়ো বড়ো কিছু পাথর আর নুড়ির মধ্যে দিয়ে পথ করে কিছুদূর বয়ে গেছে। তারপরেই শুরু হয়েছে শীর্ণ নালা প্রবাহ। ভল্লা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করল, আশপাশের জমি-জায়গা। তার মনে হল, এই সব পাথর-নুড়ি আর মাটি দিয়ে গড়ে তোলা সম্ভব দুর্বল বাঁধ। তার উজানে বানিয়ে তোলা যেতে পারে ক্ষুদ্র জলাধার। এই স্থানটির অবস্থান যেহেতু একটু উঁচুতে, অতএব ওই জলাধার থেকে কৃত্রিম নালি কেটে জলকে চারিয়ে দেওয়া যেতে পারে সংলগ্ন নাবাল জমিগুলিতে। নিষিক্ত জমিতে চাষ করা যেতে পারে কিছু কিছু উপযোগী ফসল। ভল্লা দক্ষ সৈনিক, তীক্ষ্ণবুদ্ধি গুপ্তচর। দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় সে জানে, একটি গ্রামের সকল অধিবাসীকে কখনও উত্তেজিত করা যায় না। কতিপয় মানুষ বিদ্রোহী হয়। ভল্লা জানে এই গ্রামেরও নির্বিবাদী অধিকাংশ মানুষ হয় উদাসীন থাকবে, নয়তো ক্ষুব্ধ হতে থাকবে ভল্লার ওপর। বিদ্রোহী ছেলেদের বাবা-মা, দাদু-ঠাকুমা পরিজন সকলেই ভল্লার ওপর ক্রুদ্ধ হতে থাকবে, তাদের ছেলেদের “মাথাগুলি চিবিয়ে খাওয়ার” জন্যে। সেই ক্রোধ কিছুটা প্রশমিত হতে পারে, গ্রামের অর্থনৈতিক কিছু উন্নতির দিশা দেখাতে পারলে। সামান্য হলেও, ওই জলাধার এবং উদ্বৃত্ত কিছু ফসলযোগ্য জমির সৃজন, বাড়িয়ে তুলবে ভল্লার বিশ্বাসযোগ্যতা এবং গ্রহণযোগ্যতা। সন্ধ্যার কিছু আগে ভল্লা আগের জায়গাতেই ফিরে এল। সূর্য অস্ত গেলেও পশ্চিমদিগন্তে তার আলোর রেশ এখনও রয়েছে। বড়ো গাছের নিচে বসতে গিয়ে দেখল, তিনজন ছোকরা মাটিতে শুয়ে আছে। হাপরের মতো ওঠানামা করছে তাদের বুকগুলো। ভল্লা খুশি হল, কিন্তু চেঁচিয়ে ধমক দিল তিনজনকেই। বলল, “দৌড়ে এসে হাঁফাচ্ছিস, কিন্তু শুয়ে শুয়ে হাঁফাচ্ছিস কেন? একজায়গায় দাঁড়িয়ে কিংবা বসে হাঁফানো যায় না? ওঠ, উঠে বস। এতক্ষণের পরিশ্রমে পুরো জল ঢেলে দিলি, হতভাগারা”। ভল্লার কথায় তিনজনেই উঠে বসল এবং হাঁফাতে লাগল। ভল্লা বলল, “ধর শত্রুপক্ষের তাড়া খেয়ে, এ অব্দি নিরাপদেই এসেছিস। কিন্তু এরপর কী করবি?”“ওফ্। আগে একটু দম নিতে দাও ভল্লাদাদা”।ভল্লা আবারও ধমকে উঠল, “না, দম নিতে হবে, তার সঙ্গে ভাবনা চিন্তাও করতে হবে”। এই সময় আরও পাঁচজন ছেলে পৌঁছল। ভল্লা বলল, “বাঃ, প্রথম দিনেরপক্ষে ভালই – চল আমরা এসসঙ্গে নামতা বলি...এক এক্কে এক, এক দুগুণে দুই...জোরে জোরে চেঁচিয়ে...সবাই একসঙ্গে”। সন্ধের আগেই বাইশ জন এসে পৌঁছল, আরেকটু পরে পৌঁছল আরও বারো জন। সকলে একটু ধাতস্থ হতে ভল্লা বলল, “বিয়াল্লিশ জন ফিরেছিস দেখছি, বাকিরা?”“ওরা সরোবর অব্দি গিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে নামেনি, ফিরে আসছে গ্রামের পথেই”। ভল্লা হাসল, “এরকম রোজ দুবেলা দৌড়তে পারবি? খুব ভোরে আর আজকের মতো বিকেলে?” “পারবো”। “ঘোড়ার ডিম পারবি। কাল সকালে গায়ের ব্যথায় উঠতেই পারবি না। বোনকে দিয়ে গা-হাত-পা টেপাবি”।“পারবো”। কেউ কেউ বলল, কিন্তু তাদের গলায় আগেকার সে জোর নেই। ভল্লা হাসল, “কাল সকালে পায়ে, গায়ে, কাঁধে ব্যথা হবে। হবেই। কিন্তু কালকেও দৌড়তেই হবে, আজকের মতো এত তাড়াতাড়ি না হলেও – হাল্কা ছন্দে। একটু দৌড়লেই দেখবি – গায়ের ব্যথা কমে যাবে – কষ্ট কমে যাবে। আর দৌড়তে দৌড়তেও ভাববি, চিন্তা করবি – যা খুশি, যা তোর মন চায়। মনে রাখিস দৌড়লে আমাদের সর্বাঙ্গের পেশীর শক্তি বাড়ে। শক্তি বাড়ে আমাদের ফুসফুসের, আমাদের হৃদয়ের। কিন্তু মস্তিষ্ক? তার কী হবে? ভয়ংকর পরিশ্রমের মধ্যে, প্রচণ্ড আতঙ্কে, ভীষণ ক্লান্তিতেও আমাদের মাথা যেন কখনো অলস না থাকে। কোন কিছু না পেলে আমাকেই খুব গালাগাল দিবি। ভাববি কি কুক্ষণেই না ভল্লাদাদার কাছে গিয়েছিলাম। শয়তান লোকটা আমাদের সবাইকে খাটিয়ে মারছে, আর নিজে বসে বসে শুধু উপদেশ দিয়ে যাচ্ছে। ও হ্যাঁ, কাল সকালে আমিও তোদের সঙ্গে দৌড়বো। কমলিমায়ের যত্নে শরীরটা বড়ো অলস হয়ে উঠেছে – সেটাকে আবার চাঙ্গা করতে হবে”। অন্যদিনের তুলনায় আজ বাড়ি ফিরতে একটু দেরিই হল জুজাকের। কমলি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন – বারবার বেরিয়ে বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে গলা বাড়িয়ে পথের দিকে তাকিয়ে দেখছিলেন, মানুষটা আসছে কিনা। আজ অমাবস্যা। দুপাশের গাছপালা, ঝোপঝাড়ে গভীর অন্ধকার। তারার আলোয় পথটাকেই অস্পষ্ট ঠাহর করা যায়। পথের প্রেক্ষাপটে মানুষের অবয়ব বুঝতে পারা যায়। কমলির উদ্বেগ বাড়ছিল, জুজাক গ্রামপ্রধান ঠিকই, তবে তিনি শুনেছেন রাজধানী থেকে আসা রাজকর্মচারীরা অনেক ক্ষেত্রেই গ্রামপ্রধানকে সমীহ করে না। তারওপর জুজাক কিছুটা মুখফোঁড় বদরাগীও বটে। আধিকারিকদের কোনো তির্যক প্রশ্নের ব্যাঁকা উত্তর দিয়ে, পরিস্থিতি উত্তপ্ত করে তুলতে তার জুড়ি নেই। তার এই স্পষ্টবাদী সরল চরিত্রের জন্যেই গ্রামের মানুষ তাকে শ্রদ্ধা করে গ্রামপ্রধান বানিয়েছে। জুজাকের জন্য একদিকে কমলি যেমন গর্ব অনুভব করেন, অন্যদিকে ততটাই শঙ্কিতও থাকেন সর্বদা। তিনি জানেন দিনকাল বদলে চলেছে নিরন্তর। অপ্রিয় সত্যকথা কেউই সহ্য করতে পারে না। প্রশাসনিক আধিকারিকরা তো নয়ই। আজ অন্য আরেকটি বিষয়ও কমলির দুশ্চিন্তাকে বাড়িয়ে তুলেছে। ভল্লা। আজ গ্রামে সকলের সামনে সে নিজের মুখেই স্বীকার করেছে তার অপরাধের কথা। তার নির্বাসন দণ্ডের কথা। রাজকর্মচারীদের কাছে কী সে সংবাদ পৌঁছে গিয়েছে? যদি তারা জেনে গিয়ে থাকে ভল্লা জুজাকের ঘরেই আশ্রয় পেয়েছে। এই ঘরেই সে চিকিৎসা এবং সেবা পেয়ে সুস্থ হয়ে উঠেছে। সেটা কি তারা রাজদ্রোহীতা বলে মনে করবে? জুজাককে শাস্তি দেবে? কশাঘাত করবে? কিংবা বন্দী করে রক্ষীদের দিয়ে শারীরিক অত্যাচার করবে?হতভাগা ছেলেটা গেলই বা কোথায় কে জানে? নিজের ঘরে কিছুক্ষণ শুয়ে থেকে “আমি একটু ঘুরে আসছি, মা” বলে বেরিয়েছিল শেষ দুপুরে। এখনও পর্যন্ত তারও দেখা নেই। ঘরে থাকলে, একটু এগিয়ে গিয়ে দেখে আসতে পারত ছেলেটা। জুজাকের সঙ্গে যারা গিয়েছিল তাদের বাড়ি গিয়েও খবর আনতে পারত। বলা যায় না, জুজাক হয়তো, তাদের কারো বাড়িতে বসে জমিয়ে গল্প করছে। লোকটার কাণ্ডজ্ঞান ওরকমই। তার জন্যে ঘরে যে কেউ উৎকণ্ঠায় বসে আছে, সে কথা তার মনেই পড়ে না। ঘরবার করতে করতে কমলি লক্ষ্য করলেন, তুলসীমঞ্চের প্রদীপে তেল ফুরিয়ে এসেছে, সলতেটা ম্লান হয়ে জ্বলছে। দৌড়ে গিয়ে ঘর থেকে রেডির তেল এনে প্রদীপে ঢাললেন, সলতেটা একটু উস্কে দিলেন। আর তখনই বেড়ার দরজা খোলার শব্দ হল, চমকে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন, জুজাক ঢুকছেন। “এত রাত হল? কিছু গোলমাল হয়নি তো?”জুজাক কোন উত্তর দিলেন না, ঘোঁত করে নাকে শব্দ করে, দাওয়ায় বসলেন। কমলি দৌড়ে গিয়ে ঘটি করে পা ধোয়ার জল আনলেন। ঘর থেকে নিয়ে এলেন জুজাকের গামছাখানা। জুজাক ঘটির জলে পা ধোয়া শুরু করতে, কমলি বললেন, “কিছু বললে না, তো? এত দেরি হল কেন?”দুই পা ধুয়ে, গামছা দিয়ে ধীরেসুস্থে পা মুছতে মুছতে জুজাক বললেন, “গাঁয়ে ফিরেছি অনেকক্ষণ। ও পাড়ায় ঢুকতেই লোকজনের মুখে তোমার ছেলের গুণকীর্তন শুনছিলাম। তুমি শুনেছ?”“শুনেছি”।“তা আর শুনবে না? তোমার আদরের ছেলের জন্যে কাছারিবাড়িতেও আমাকে কত কথা শুনতে হল। খাবার জল দাও তো”। কমলি ঘর থেকে খাবার জল এনে দিলেন। “কী বলেছে তারা?”জুজাক মাটির ঘটি হাতে তুলে নিয়ে নিঃশেষ করলেন ঘটিটা। তারপর তৃপ্তির শ্বাস ছেড়ে বললেন, “হবে আর কী? গিয়েছিলাম কান্নাকাটি করে এ গ্রামের মানুষদের কিছুটা কর যদি কমানো যায়। অন্ততঃ সম্বৎসর সকলের পেটটা যাতে চলে যায়। সে কথায় কানই দিল না? বললে, ভল্লা তোমার বাড়িতে আছে? বললাম, আছে। বললে, একজন অপরাধী – যার রাজধানীর প্রশাসন থেকে নির্বাসন দণ্ড ঘোষণা হয়েছে। তাকে তুমি বহাল তবিয়তে খাওয়াচ্ছো, দাওয়াচ্ছো, চিকিৎসা করাচ্ছো। আর রাজার কর দিতেই তোমার নাকে কান্না শুরু হয়ে গেল?”কমলি উদ্বেগের স্বরে বললেন, “কী অবস্থায় ছেলেটা এসেছিল তুমি বললে না?”জুজাক একটু ঝেঁজে উঠে বললেন, “বলব না কেন? সবই বলেছি”। তারপর একটু থেমে নরম স্বরে বললেন, “ওরা রাজ কর্মচারী। তাদের কাছে ভল্লার পরিচয় অপরাধী। সে আর মানুষ নয়, জন্তু। ওদের কথা, ঘেয়ো কুকুরের মত যেভাবে এসেছিল, সেভাবেই ওকে তাড়িয়ে দিইনি কেন? জগৎটা তোমার মতো মায়ের মন নিয়ে যে চলে না, কমলি”।কমলি জুজাকের সহানুভূতির সুরে আশ্বস্ত হলেন। মানুষটাকে ওপরে ওপরে কঠোর মনে হলেও, মনটা নরম। তা যদি না হত, জুজাক জোর করেই ভল্লাকে তাড়িয়ে দিতে পারতেন। তৎক্ষণাৎ না হলেও, যেদিন ভল্লার প্রথম জ্ঞান হল, সেদিনই। আজকে রাজ-প্রতিনিধির যে তিরষ্কার তিনি শুনে এলেন – এমন যে হবে সেকথা জুজাক বহুবার বলেছেন। বারবার বলেওছেন, হতভাগাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেব – কিন্তু দিতে পারেননি। মানবিক বোধের কাছে তার বাস্তব যুক্তি হার মেনেছে। কমলি জিজ্ঞাসা করলেন, “কিন্তু ওদের কাছে এ খবর পৌঁছে দিল কে? নিশ্চই এই গাঁয়েরই কেউ?”“সে তো বটেই। সব গ্রামেই ওদের গুপ্তচর থাকে। তাদের কাজই তো ওদের খবর দেওয়া। সে যাক, ছোঁড়াটাকে ডাক দেখি একবার”।“সে তো সেই দুপুরের দিকে বেরিয়ে গেছে, এখনও ফেরেনি”।“কোথায় গিয়েছে তোমাকে বলেও যায়নি? আশ্চর্য। কবিরাজদাদার বাড়িতে আমরা বেশ কয়েকজন কথাবার্তা বলছিলাম। সেখানে শুনলাম, সকালে ভল্লার বক্তৃতা শুনে কয়েকজন ছোকরা নাকি বেশ বিগড়ে গেছে। দুপুরের পর থেকেই তারাও বাড়িতে নেই। তবে কি...”।কমলি আতঙ্কিত হয়ে বললেন, “তবে কি গো? ওই ছোঁড়াগুলো কি ভল্লাকে মারধোর করবে?”জুজাক হেসে ফেললেন কমলির সরলতায়, বললেন, “মেয়েদের লাঞ্ছনা রোধ করতে গিয়ে সে অপরাধী হয়েছে। রাজ-প্রশাসন লম্পট মানুষটাকে শাস্তি না দিয়ে, সাজা দিয়েছে ভল্লাকে। এ গাঁয়ের ছোকরাদের চোখে ভল্লা এখন বীর-নায়ক। কবিরাজদাদা বলছিলেন, ভল্লা বোধ হয় ছোকরাদের নিয়ে একটা দল গড়তে চাইছে”।কমলি অবাক হয়ে বললেন, “কিসের দল?”জুজাক আবার একটু ঝেঁজে উঠলেন, বললেন, “তার আমি কী জানি? তোমার মনে আছে, কবিরাজদাদা ওর শরীরের লক্ষণ দেখে বলেছিলেন, ভল্লা সাধারণ এলেবেলে ছেলে নয়। যথেষ্ট শক্তিশালী যোদ্ধা। আরও বলেছিলেন, ওই চরম অসুস্থ অবস্থায় ওর এখানে আসাটা হয়তো আকস্মিক নয়। হয়তো গোপন কোন উদ্দেশ্য আছে। আজকে সকলের সামনে কবিরাজদাদা সে প্রসঙ্গ তোলেননি। কিন্তু আমারও এখন মনে হচ্ছে কবিরাজদাদার কথাই ঠিক”।কমলি কিছু বললেন না। হাঁটুতে থুতনি রেখে গভীর চিন্তা করতে লাগলেন, ভল্লাকে দেখে কই আমার তো তেমন কিছু মনে হয়নি। এ গ্রামে আসা থেকে আমি তাকে যত কাছে থেকে দেখেছি, আর কে দেখেছে? তার কথাবার্তায়, তার মা ডাকে কোথাও কোন উদ্দেশ্যর সন্ধান তো তিনি পাননি। আজকে গ্রামের সবার সামনে মন খুলে নিজের অপরাধের কথা যে ভাবে সে স্বীকার করেছে, তার মনে যদি সত্যিই কোন পাপ বা অপরাধ বোধ থাকত, পারত ওভাবে বলতে?জুজাক বললেন, “খাবার বাড়ো, খেয়ে শুয়ে পড়ি”।কমলি তাড়াতাড়ি উঠে খাবার আনতে ঘরে ঢুকলেন। সেদিকে তাকিয়ে জুজাক বললেন, “তোমার ছেলে যত রাতই হোক বাড়িতে তো ঢুকবেই। তুমি ছাড়া তার জন্যে কে আর রাত জেগে খাবার কোলে বসে থাকবে? এলে বলে দিও, সামনের অষ্টমীতে ওকে সঙ্গে নিয়ে আমাকে কাছারি শিবিরে যেতে হবে। বলে দিও, না গেলে ওর তো বিপদ হবেই, আমাদেরও রক্ষা থাকবে না”।ক্রমশ...ফৈজান আহমেদ আত্মহত্যা করেন নি - অমিতাভ চক্রবর্ত্তী | ছবি: রমিত চট্টোপাধ্যায়নির্মম হত্যাকান্ড! খুন হয়েছিলেন ফৈজান আহমেদ? কি ভাবে? গত ২১শে মে ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ ডক্টর অজয় গুপ্তা কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর বেঞ্চকে জানান যে ফৈজানকে মাথার পিছনে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হয়েছিল, ঘাড়ের জায়গায় ছুরির আঘাত করা হয়েছিল এবং তার পর পিছন থেকে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে ঘাড়ে গুলি করা হয়েছিল। (১৩-ই জুনের ই-নিউজরুম ইন্ডিয়ার প্রকাশিত সংবাদ)এই রিপোর্ট মৃতদেহের দ্বিতীর ময়নাতদন্তের ফল।কেন দু’বার ময়নাতদন্ত? কারণ, প্রথম ময়নাতদন্তে এতগুলি চিহ্নর কোন কিছু নজরে আসে নি আর মৃত্যুর কারণ সাব্যস্ত হয়েছিল আত্মহত্যা। ফৈজান আহমেদ, আই আই টি খড়গপুরের মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। আসামের তিনসুকিয়া থেকে অনেক স্বপ্ন নিয়ে প্রতিভাবান ছাত্রটি পড়তে এসেছিলেন সেখানে। ২০২২-এর অক্টোবর ১৪ তারিখে নিজের হস্টেল ঘর থেকে ২৩ বছরের ছেলেটির অর্ধ-গলিত মৃতদেহ পাওয়া গেল। আই আই টি কর্তৃপক্ষ এবং পুলিশের বক্তব্য অনুসারে তিনি আত্মহত্যা করেছেন।ফৈজানের মৃত্যুর খবর পেয়ে তার পরিবার খড়গপুরে পৌঁছে তার মৃতদেহ দেখে এই মৃত্যুকে আত্মহত্যা বলে মানতে অস্বীকার করেন। তারা বলেন ফৈজান র্যাগিংয়ের শিকার এবং তিনি খুন হয়েছেন। পুলিশ ময়নাতদন্তের রিপোর্ট থেকে জানায় যে ঠিক কি ভাবে মৃত্যু হয়েছে সেটা বলতে না পারা গেলেও তারা নিশ্চিত যে এটি আত্মহত্যার ঘটনা।ফৈজানের মা-বাবা কলকাতা হাইকোর্টে পিটিশন দাখিল করেন। পোস্ট-মর্টেম রিপোর্টে অসঙ্গতি নজরে আসায় হাইকোর্ট মৃতদেহ কবর থেকে তুলে নিয়ে এসে দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্ত করার আদেশ দেয়। দ্বিতীয় ময়নাতদন্ত কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে মৃত্যুর কারণ জানতে চেয়ে অবসরপ্রাপ্ত ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ ডক্টর অজয় কুমার গুপ্তা মৃতদেহের দ্বিতীয়বার পোস্ট-মর্টেম করলেন। পরীক্ষা শেষে তার প্রাথমিক রিপোর্টে তিনি জানালেন যে তিনি মৃতদেহের মাথার পিছন দিকে দুটি আঘাতের চিহ্ন পেয়েছেন। বুকে আর মাথায় প্রচুর রক্তক্ষরণের ফলে হেমরেজিক শক হয়ে তিনি মারা গেছেন।প্রথম ময়নাতদন্তের রিপোর্টে এই আঘাত চিহ্নগুলির কোন উল্লেখ ছিল না। আরও জানালেন যে মৃতদেহের হাতে যে ক্ষতচিহ্নগুলি পাওয়া গেছে সেগুলি তার মৃত্যুর পরে ঘটেছিল। এ ছাড়াও গুপ্তা জানিয়েছিলেন যে অপরাধের জায়গা থেকে সংগৃহিত বস্তুদের যে তালিকা পুলিশ বানিয়েছিল তাতে এমপ্লুরা নামওয়ালা একটি রাসায়নিকের উল্লেখ আছে। কি এই রাসায়নিকটি? কোন কাজে লাগে?কোর্ট নিয়োজিত বিশেষজ্ঞ সন্দীপ ভট্টাচার্য্য জানিয়েছিলেন যে এই রাসায়নিকটি সাধারণত মাংস ইত্যাদি সংরক্ষণের জন্য ব্যবহার করা হয়। গুপ্তা এবং ভট্টাচার্য্য দুজনেই জানান যে তারা মৃতের ঘরে একটি পাত্রে এই রাসায়নিকটির রংয়ের কোন কিছুর অবশেষ দেখতে পেয়েছেন। কোর্টকে আরও একটি অবাক হওয়ার মত ব্যাপার জানানো হয়েছিল যে যদিও মৃতদেহ গলে-পচে গেলে তার থেকে দুর্গন্ধ বের হওয়া একটি স্বাভাবিক ঘটনা, তিন দিন ধরে কাছাকাছি ঘরের অন্যান্য বাসিন্দারা গলে পচে যাওয়া মৃতদেহের থেকে কোন গন্ধ পাননি।Special Investigation Team (SIT) বিচারপতি রাজশেখর মান্থা সিনিয়র আই পি এস অফিসার এস জয়ারমণের নেতৃত্বে তিন সদস্যের একটি বিশেষ তদন্তকারি দল (সিট), Special Investigation Team (SIT) গঠন করেন এবং জানান যে এই মৃত্যুকে খুন হিসাবে ধরে তদন্ত পরিচালনা করতে হবে। আই আই টি খড়গপুর কর্তৃপক্ষ এবং কলকাতা পুলিশ সিট-কে দিয়ে তদন্ত চালানোর বিরোধিতা করে ডিভিশন বেঞ্চে যায়। কিন্তু প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্য্যর ডিভিশন বেঞ্চ সিঙ্গল বেঞ্চের রায়টিই বহাল রাখে। তারা আরও বলেন যে শুধুমাত্র দ্বিতীয় ময়না-তদন্তের রিপোর্টটির ভিত্তিতেই তদন্ত হবে। তারা সিটের দলটি থেকে নেতা ছাড়া বাকি দুজনকে সরিয়ে দেন এবং নেতাকে তার পছন্দমতো সহকারি বেছে নিতে বলেন। সিট তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যায়, কিন্তু আত্মহত্যার লাইন ধরে এবং এত ধীর গতিতে আর আই আই টি কর্তৃপক্ষের কথা মেনে যে বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত তাদের কাজের গতি-পদ্ধতি নিয়ে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তদন্তের অগ্রগতির জন্য সময়সীমা সহ একাধিক নির্দেশ দেন। সাম্প্রতিক রিপোর্ট ২১শে মে বিচারপতি সেনগুপ্ত যে রিপোর্ট পেলেন তার থেকে আশা করা যায় যে এখন থেকে ফৈজানের মৃত্যু হত্যা বলেই বিবেচিত হবে, আত্মহত্যা নয়। নামকরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে পড়ার চাপ সইতে না পেরে বা অন্য কোন কারণে ছাত্ররা আত্মহননের পথ বেছে নেন কখনো কখনো। অস্বাভাবিক মৃত্যুগুলি আত্মহত্যার কারণে হয়েছে জানা গেলে অনেকের অনেক কাজ বেঁচে যায়। নিজের ছাড়া অন্য কারো হাতে মারা গেলে অর্থাৎ র্যাগিং বা অন্য কোন কারণে খুন হয়ে থাকলে খুনীকে খুঁজে বার করার, তাকে শাস্তি দেওয়ার ইত্যাদি নানা দায়িত্বের কাজ এসে পড়ে। তারপর কে জানে, কোন সুতো ধরে কোথায় টান পড়ে যাবে, কার মুখোশ খুলে যাবে। আত্মহত্যা সাব্যস্ত হয়ে গেলে আর এই সব অশান্তি থাকে না। আই আই টি খড়গপুর কর্তৃপক্ষ, কলকাতা পুলিশ এবং ধীরগতিতে চলা সিট, এদের সকলের কাজের প্রতিকূল প্রভাব অতিক্রম করে এবার কি অপরাধী ধরা পড়বে? ফৈজানের মা-বাবার একমাত্র ছেলেটির খুনীর শাস্তি হবে কি?সূত্র সমূহ:https://www.ndtv.com/india-news/decomposed-body-of-iit-kharagpur-student-recovered-from-hostel-room-3432443#:~:text=A%20semi-decomposed%20body%20of%20an%20Indian%20Institute%20of,into%20the%20hostel%20recently%2C%20according%20IIT%20Kharagpur%20authorities.https://www.newindianexpress.com/nation/2023/Jun/07/iit-kharagpur-studentfaizan-ahmeds-death-was-ahomicide-second-autopsy-report-2582731.htmlhttps://www.ndtv.com/india-news/iit-kharagpur-faizan-ahmed-death-iit-kharagpur-students-2nd-autopsy-shows-homicidal-injuries-sources-4113714https://enewsroom.in/calcutta-high-court-ragging-in-iit-kharagpur-faizan-ahmed/https://enewsroom.in/iit-kharagpur-murder-investigation-faizan-ahmed-iitian/https://enewsroom.in/iit-kgp-kharagpur-faizan-ahmed-iitian-murder/
হরিদাস পালেরা...
বৈঠকি আড্ডায় ১৮ - হীরেন সিংহরায় | বৈঠকি আড্ডায় ১৮ গরুর গাড়ির গতি বাড়ালেই মোটর* গতির গেট“ ঘণ্টায় সর্বোচ্চ তিরিশ মাইল বেগে চালনার জন্য নির্দিষ্ট এলাকায় আপনি পঁয়ত্রিশ মাইল গতিতে গাড়ি চালিয়েছেন। আপনার অবগতির জন্য অপরাধের দিন, সময় এবং গাড়ির রেজিস্ট্রেশন নম্বর প্লেটের ছবি এই পেনাল্টি নোটিসের সঙ্গে সংযোজিত হলো। এ চিঠি পাবার পনেরো দিনের মধ্যে পেনাল্টি পরিমাণ চেক বা অন লাইনে প্রদেয়। বিলম্বে জরিমানা।আপনি যদি এই গাড়ি তখন না চালিয়ে থাকেন বা এই গতিসীমা উল্লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে আপনার অন্য কোন প্রতিবাদ থাকলে এই ঠিকানায় আপন বক্তব্য পেশ করতে পারেন । আমরা সে বিষয়টি প্রণিধান করব ।"দিন তারিখ ও ছবি দেখে বুঝলাম অকুস্থল আমাদের পাশের ছোটো শহর সানিংডেল। ঘটনার দিন মেয়ের সঙ্গে দেখা করে এগহ্যামের রয়্যাল হলওয়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিরছিলাম । বনপথে উচ্চতম ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল বেগে গাড়ি চালানোর নির্দেশ দেওয়া আছে কিন্তু সানিংডেল ঢোকার পাঁচশ মিটার আগে হঠাৎ সেই গতিসীমা দশ মাইল কমে যায় । যেখানে সন্ধ্যে হয় মানে ঠিক ওই নোটিসের পাশেই শীর্ণ পিলারের মাথায় একটি হরিৎ বর্ণের ছোট বাকসো অনেকটা উটের গ্রীবার মতো কৌতূহলী ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুতুল নাচের ইতিকথায় হারু ঘোষের দিকে আকাশের দেবতা কটাক্ষ করেছিলেন এখানেও সেই রকম এক যান্ত্রিক কটাক্ষের ফলে আমার গাড়িটি ঝলসিয়া না গেলেও চিত্রায়িত হইল । এটি তার শাস্তি – এবার ফাইন এবং ড্রাইভিং লাইসেন্সে তিনটে পয়েন্ট যোগ হবে। এই প্রক্রিয়া চালু রেখে আগামী তিন বছরের মধ্যে এক ডজন পয়েন্ট অর্জন করলে আমার লাইসেন্স বাতিল হবে।উটের গ্রীবার মতপুলিশের চিঠির পরের পাতায় একটি চমকের সম্মুখীন হতে হলো। আমার পরিণত বয়সের কথা বিবেচনা করে তাঁরা আমাকে একটি দ্বিতীয় প্রস্তাব দিচ্ছেন – আমি যদি পুলিশ কর্তৃপক্ষ আয়োজিত গাড়ির গতি বিষয়ক সচেতনতার একটি কোর্স সাফল্যের সঙ্গে সমাপ্ত করতে পারি তাহলে ফাইন দিতে হবে না , লাইসেন্সে পয়েন্ট যোগ হবে না। এমনকি আমার গাড়ির ইন্সিউরেনস কোম্পানি আমার এই পদস্খলনের উপাখ্যান অবধি জানবেন না( এই দুষ্কর্মের কাহিনি চাউর হলে তাঁরা আমার বিমার প্রিমিয়াম বাড়িয়ে দিতে পারেন ) । সামনের চার মাসের মধ্যে আমার বাড়ির নিকটবর্তী শিক্ষাকেন্দ্রে চার ঘণ্টার ক্লাস করতে হবে , ইন্টারনেটে বেছে নিন কোনদিন আপনার সুবিধে : দক্ষিণা নব্বুই পাউনড।ঘোড়া জোতা ফিটনের উচ্চতম গতি কোথায় বাঁধা ছিল জানি না তবে মোটর গাড়ির আবির্ভাবের পরে গত শতাব্দীর গোড়ায় ইংল্যান্ডে প্রথম আইনি গতিসীমা ছিল ঘণ্টায় চৌদ্দ পরে কুড়ি মাইল । কোন যন্ত্রপাতি নয়, স্টপ ওয়াচ হাতে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থাকা পুলিশ অনুমান করতো কোন গতিতে একটি গাড়ি দুটি নির্দিষ্ট পয়েন্ট অতিক্রম করেছে। তাই দিয়ে জরিমানা ধার্য হতো । লর্ড মনটেগু মন্তব্য করেন এটি হাইওয়ে রবারি !কত দ্রুত বেগে গাড়ি চলছে সেটা মাপার জন্য স্পিডক্যামেরার আবিষ্কার হয় নি। হয়েছে ঠিক তার উলটো কারণে। মাউরিস গাটসোনিদেস নামের এক ডাচ রেসিং ড্রাইভার নিজের গাড়ির স্পিডোমিটারের সঙ্গে একটি পালস মাপার যন্ত্র লাগিয়ে দেখতে চাইলেন মোড় নেওয়ার সময়ে তাঁর গাড়ির গতি কতোটা কমাতে সক্ষম হচ্ছেন। ঠিকমত না কমাতে পারলে অঘটনের সম্ভাবনা। পরে সেই আইডিয়া থেকে তিনি বানালেন পথে পথে ধাবিত গাড়ির গতি মাপতে সক্ষম এক ক্যামেরা তার নাম হল গাটসোমিটার । ১৯৬৪ সালে ডাচ পুলিশের কোন তৎপর করিতকর্মা মানুষ ভাবলেন, এই মউকা পাওয়া গেল টাকা আদায়ের। সেই ক্যামেরাকে কাজে লাগিয়ে লর্ড মনটেগুর হাইওয়ে রবারিকে সম্পূর্ণ আইন সম্মত করে সরকারের রাজকোষ ভরে তোলার যে তরিকা ডাচেরা চালু করলেন, ইউরোপের সব দেশ তাকে হামলে নিলো ! ব্রিটেনে অবশ্য কিছু বিলম্বে , এই মাত্র ১৯৮০ সালে প্রথম স্পিডক্যামেরা বসানো হয় । আশ্চর্যের বিষয় কিছু নয়- এদেশে যখন এসেছি, এই চল্লিশ বছর আগে, সিট বেল্ট বাঁধা আবশ্যিক হলো , তাও কেবল ড্রাইভার ও সহ যাত্রীর জন্য ; বাকিদের সিটবেল্ট পরার নির্দেশ এলো আরও কয়েক বছর বাদে । জার্মানিতে গাড়ি চড়লেই বেল্ট বাঁধতে হতো সেই ১৯৭৫ সালে। ভাবলাম নব্বুই পাউনড খরচা করলে যদি শাস্তিমূলক কোন পয়েন্ট যোগ না হয় তাহলে ক্লাসে না হয় চার ঘণ্টা বসে গতি বিষয়ে সচেতনতা অর্জন করে আসি। আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স জার্মানির – সে দেশে একটা লিখিত পরীক্ষা পাশ করলে তবেই নিরীক্ষকের তত্ত্বাবধানে বসে গাড়ি চালানো শেখা সম্ভব ( ইংল্যান্ডে রিটন টেস্ট চালু হয়েছে বছর বিশেক আগে ) ; জার্মান লাইসেন্স আজীবনের । যখন ব্রিটেনে এলাম আমার সেই লাইসেন্স অনুবাদ করিয়ে এ দেশের মোটর ভেহিকল দফতরে জমা দিয়ে পেলাম ব্রিটেনে গাড়ি চালানোর আইনি অধিকার। সেটি ৬৫ বছর বয়েস অবধি ভ্যালিড তার পর বছর পাঁচেক অন্তর রিনিউ করাতে হবে ! তাঁরা অবশ্য আমাকে সান্ত্বনা দিলেন আমার আদি লাইসেন্স তাঁদের হেপাজতে রইল । আমি কখনো দেশ ত্যাগ করলে সেই জার্মান লাইসেন্স তাঁরা অক্ষত অবস্থায় ফেরত দেবেন ।ফ্রাঙ্কফুর্টে আমার ড্রাইভিং শিক্ষাগুরু কার্ল বলতেন ,’ যা শেখাচ্ছি তার অর্ধেকও মনে রাখবেন না পরে , কিন্তু কেতাবি আইনগুলো জেনে রাখুন। ফলে কোন আইনটা যে ভাঙ্গছেন সেটা নিজেই বুঝবেন , ধরা না পড়লেই হলো ।‘ স্থানীয় জেলা সদর গিলডফোরডে গতি সচেতনতার কেলাসে বসে বুঝলাম কার্লের কথা কতোটা সত্যি ছিল । একে তো আমার গাড়ি চালানোর কেতাবি শিক্ষা ব্রিটেনের নয় , হাইওয়ে কোড নামক বিলিতি বাইবেল পাঠ করি নি। তাই রাস্তায় ল্যাম্প পোস্ট থাকলেই যে তিরিশ মাইল গতি সীমা বাঁধা সেটা জানি না । মনে আছে জার্মানিতে শহর /গ্রামের মধ্যে (ইনারহালব গেশ্লসেনে অরটশাফট ) কত কিলোমিটার স্পিডে চালাতে পারি তার নির্দেশ সূচক সাইনবোর্ড দেওয়া আছে, তা সেখানে ল্যাম্প পোস্ট থাকুক আর নাই থাকুক । গতি শিক্ষা ক্লাসের মধ্যিখানে চায়ের বিরতি ছিল -সেই সময় লক্ষ করলাম উদ্ধত যত শাখার শিখরে রডোড্রেনডন গুচ্ছের সন্ধানে ধাবিত আঠারো কুড়ি বছরের কোনো যুবক যুবতী নয়, আমার কমরেডস ইন ক্রাইম প্রায় সকলেই মধ্য বা আমার মতন পরিপক্ব বয়েসি । এমন জায়গায় অনায়াসে জানতে চাওয়া যায় কে কোথায় কোন আইন ভঙ্গ করে এই করেকশনাল কারাগারে এয়েছেন । আমার মতন সকলেই কোন গ্রামে গঞ্জে গতি নিয়ম ভেঙ্গেছেন , ওই পাঁচ সাত মাইল বেশি ; কেউ পেরেনট-টিচার মিটিঙে সময়মত পৌঁছুনোর তাড়ায় , কেউ ডাক্তার দেখাতে। মোটরওয়ের খোলা হাওয়ার পালে গা এবং গাড়ি ভাসিয়ে , নিছক আইন ভাঙার আনন্দে কেউ অ্যাকসিলারেটর দাবান নি ।ট্রাফিক লাইটের সঙ্গী ক্যামেরাশিক্ষক রবার্ট অত্যন্ত ভালমানুষ । তাঁর কেলাসে পাশ ফেল নেই , নব্বুই পাউনড এবং হাজিরা দিলেই তিনি সন্তুষ্ট। কাউকে সরাসরি কোন প্রশ্ন করে বিড়ম্বনায় ফেলেন না – বড়জোর জিজ্ঞাসার বল হাওয়ায় ভাসিয়ে দেন – যার ইচ্ছে সে সেই বলটা তুলে নিক । রাস্তায় ল্যাম্প পোস্ট না থাকলেও কোন রাস্তায় কোন স্পিডে গাড়ি চালানোর নিয়ম সেটা যে অধিকাংশ সময়ে পথের দুপাশে দুটি বিশাল ললিপপের মতন বোর্ডে সাজানো থাকে, তার নাম যে গেট সে তথ্য জেনে ধন্য হলাম। চেষ্টা না করেও কিছু প্রাসঙ্গিক তথ্য গোচরে এলো – গোটা সারে জিলায় সেই মুহূর্তে ১২১টা স্পিডক্যামেরা আছে । কিন্তু যে কোন সময়ে মাত্র ৭১টি ক্যামেরায় ফিল্ম বা মেমরি কার্ড থাকে, অন্যগুলোতে ফ্ল্যাশ হয় কিন্তু ছবি ওঠে না । এই আমার প্রশ্ন করার সুযোগ – যদি ছবি না উঠবে তাহলে ক্যামেরার কাজ কি ? রবার্ট স্মিতমুখে বললেন , কোনো গাড়ি গতি সীমার ঊর্ধ্বে চালিত হলে , ফিল্ম থাকুক না থাকুক ক্যামেরা ফ্ল্যাশ করবে । আপনি তো জানেন না আপনি সত্যিকারের স্ক্রিনশট দিলেন কিনা কিন্তু ক্যামেরার ঝলকানি দেখেই আইন ভেঙ্গেছেন ভেবে অপরাধী বোধ করবেন । প্রতি মাসে একবার চেক করা হয় কোন ক্যামেরায় কতবার ফ্ল্যাশ হয়েছে। সেই হিসেবে ফিল্ম বা মেমরি কার্ড যোগ বিয়োগ করা হয় । আপনি যেখানে ধরা পড়েছেন সেখানে লাগানো ক্যামেরায় ছবি ওঠার চান্স অঙ্কের হিসেবে ষাট পারসেন্ট। কিন্তু সেদিন আপনার ভাগ্য খারাপ ছিলো । তবে লক্ষ রাখবেন সারের বহু ট্রাফিক লাইটেও ক্যামেরা লাগানো হচ্ছে , সেটা স্পিড মাপার এবং কেউ রেড লাইট জাম্প করলো কিনা দেখার জন্য। সেই অপরাধের তাৎক্ষনিক দণ্ড তিনটে পয়েন্ট । আমার ছেলে ইন্দ্রনীল ছোটবেলায় বলতো পয়সা খরচা করে ক্যামেরা বসানোর কি দরকার , তার ছবি দিলেই তো লোকে সাবধান হবে ! ভাববে ছবি উঠতে পারে। এখন মোটরওয়েতে অনেক জায়গায় দেখি ক্যামেরার ছবি আছে- বিগ ব্রাদার ওয়াচিং ! রবার্টের কথা শুনে মনে হলো, আমার পুত্র সেটাই ভেবেছিল – বাট হি ইজ নট অলওয়েজ ওয়াচিং! কিন্তু সেই চান্স নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়।তুমি কি কেবলই ছবিক্যামেরা কোথায় কোনখানে থাকে? লুকিয়ে না প্রকাশ্যে ? তাকে চেনার উপায় কি ? এ ব্যাপারে ব্রিটিশ অত্যন্ত ভদ্র- এক সময় এ দেশে ক্যামেরা বসানো থাকতো ঘোর অরেঞ্জ রঙের পিলারের ওপরে ( এখন কটকটে হলুদ) । গোপন ক্যামেরাটি রবে না গোপনে – আপনার ফটোগ্রাফার ঠিক কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে ‘ লাইট ক্যামেরা অ্যাকশন’ বলবে সেটা আপনার অগ্রিম জেনে সতর্ক হবার সুযোগ আছে , যাতে কয়েক মুহূর্তের জন্যে আপনি নিয়মানুবর্তী সভ্য সচেতন নাগরিক হিসেবে গাড়ির গতি কমিয়ে সেই শুটিং জোন অতিক্রম করতে পারেন । একই সঙ্গে অন্ধ এবং কোন কারণে উন্মনা না হলে এই বর্ণাঢ্য ক্যামেরা বাহী পিলারটি চোখে পড়া কঠিন নয় । সে তুলনায় জার্মান পুলিশ অতীব বদমাইশ –তারা ক্যামেরা লুকিয়ে রাখে কোথাও কোনো উঁচু বাড়ির ব্যালকনিতে, কারো ছাতে, এমনকি ফ্রাঙ্কফুর্টের একটা বিশাল মোড়ে মধ্যযুগের টাওয়ারের ওপরে ( স্থানীয় খবর কাগজ সেটা ফাঁস করেছে হালে)। এই রকমের বদবুদ্ধি ইউরোপের নানান দেশ আয়ত্ত করেছে। ফরাসি সীমান্ত পার হয়ে ব্রুঘে থেকে লিয়েজ যাওয়ার মোটরওয়ে পার হয়েছি বহু বার – কোথাও কোন স্পিডক্যামেরার আভাস অবধি দেখি নি । এক গুণীজন বলেছেন , বেলজিয়ামে মোটরওয়ের মাঝের ব্যারিয়ারের হেজে নাকি সেটা লুকোনো থাকে । সে পথে আমার নিয়মিত আসা যাওয়া , তবে ছবি এখনও ওঠে নি এই যা।যারা এই গ্রীষ্মে ইউরোপে গাড়ি চালাবেন মনস্থ করেছেন তাঁদের আগাম সতর্কবাণী দিয়ে রাখি- বেশির ভাগ ক্যামেরা পাবেন মোটরওয়েতে নয়, শহরের ভেতরে মানে বিল্ট আপ এলাকায়; গড় হিসেব অনুযায়ী প্রাণঘাতী দুর্ঘটনা সেখানেই বেশি ঘটে। মনে রাখবেন তারা সরকারি কর্মীর মতো নটা থেকে ছটা কাজ করে , সন্ধ্যে হলে ক্যামেরার বিশ্রাম , অনেক দেশে উইক এন্ডেও তাদের ছুটি । স্পিড ক্যামেরা মোতায়েন করার কাজে ইতালি একবারে নুমেরো উনো। স্বাভাবিক। যে দেশে প্রত্যক্ষ কর ফাঁকি দেওয়াটা জাতীয় স্পোর্টের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে সেখানে নিজের দানাপানি যোগাড় করার জন্য সরকারকে অন্য পন্থা খুঁজতে হয় । কোনো ইতালিয়ান পৌরসভার বাৎসরিক আয়ের প্রধান আইটেম পারকিং মিটারের প্রাপ্য দেয় পূরণ না করার ফাইন এবং স্পিডিঙ জনিত জরিমানা । তারপরেই ব্রিটেনের স্থান। ইউরোপের দেশগুলি বুঝে ফেলেছে এই বাজারে খাজনা বা ট্যাক্স বাড়ানো শক্ত হলেও নাগরিকদের দ্রুত গতি বাহনের ছবি তুলে প্রভূত অর্থ অর্জন করা সম্ভব।ফিনল্যান্ডে ফাইনের পরিমাণ পূর্ব নির্ধারিত বা ফ্ল্যাট রেট নয়। আপনার মাসিক আয়ের ওপরে সেটা স্থির হয়। নির্দিষ্ট গতিবেগ উল্লঙ্ঘন করে তাঁর হারলে ডেভিডসন বাইক চালানোর জন্য নোকিয়ার এক ডিরেক্টর আনসি ভানওকির জরিমানা হয় চোদ্দ দিনের মাইনে , এক লক্ষ ইউরো! নোকিয়ার এক লোন সাইনিং অনুষ্ঠানে গল্পটি শুনি তৎকালীন সি ই ও ওলিল্লার কাছে। হল্যান্ডে নির্ধারিত গতির দ্বিগুণ বেগে চালিয়ে ধরা পড়লে আপনার বাহনটি বাজেয়াপ্ত করার অধিকার আছে ডাচ পুলিশের – শোনা যায় কোন রবিবার সকালে স্কিফোল এয়ারপোর্ট এলাকায় পুলিশ একটি ফেরারি গাড়ি তাদের খোঁয়াড়ে ভরে রাখে; চালকের গতি ছিল ঘণ্টায় দুশ কিলোমিটার ! শহরে বা গ্রামের ভেতরে ধীরে গাড়ি চালানো অবশ্যই বাঞ্ছনীয় । স্পিড ক্যামেরার পথিকৃৎ হল্যান্ড – তাঁদের দেশের ট্রাফিক পুলিস জানিয়েছে গত বছরের প্রথম চার মাসে দশ লক্ষ পেনাল্টি টিকিট ইস্যু হয়েছে তার সঙ্গে দেড় লক্ষ বিদেশি নাম্বার প্লেটের গাড়ি ( সাধু ও টুরিস্ট সাবধান !) । ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রায় সকল দেশের ট্রাফিক পুলিশ দাবি করে স্পিড ক্যামেরা লাগানোর পরে পথ দুর্ঘটনা জনিত মৃত্যুর হার অর্ধেক হয়েছে কিন্তু সকলে জানান না এ বাবদে তাঁরা কত আয় করেন । ব্যতিক্রম বেলজিয়ান পুলিস – তাঁরা জানিয়েছেন গত বছরে স্পিডিঙ ফাইন বাবদ সরকারের আয় প্রায় ছ কোটি ইউরো -কষ্ট ইনকাম রেশিও অত্যন্ত লোভনীয় । যে হারে ব্রিটেনের গ্রামাঞ্চলে ক্যামেরা বহনকারী হলুদ রঙের পিলারের সংখ্যা বাড়ছে তা দেখে অনুমান করে নিতে অসুবিধে হয় না ব্রিটিশ সরকার বাজেট ঘাটতি পূরণের জন্য ক্যামেরার জাল দেশময় বিছিয়ে দিতে তৎপর হয়েছেন ।যে কোন গাড়ির লিফলেট বা ব্রশিউর হাতে তুলে দেখি - তাতে কত না গুণের ব্যাখ্যান – কিলোমিটারে কতো সামান্য তেল খায় , মেটালিক রঙ, অটোমেটিক গিয়ার, ব্রেকিং সিস্টেম ( এ বি এস ) , ছটা স্পিকার , মাত্র দশ সেকেন্ডে সে গাড়ির গতি শূন্য থেকে একশো কিলো মিটারে পৌঁছুতে সক্ষম। গাড়ির ড্যাশ বোর্ডের স্পিডোমিটার দেখলে জানা যায় তার উচ্চতম গতি বেগ ঘণ্টায় দুশো কিলোমিটার । এই সব মূল্যবান তথ্য জানিয়ে বিক্রেতারা মহার্ঘ্য গাড়ি বিক্রি করেন ।সে যে মানে সব মানাগাড়ির শো রুম থেকে বেরুলেই চোখে পড়ে নোটিস - শহরের ভেতরে গাড়ির গতির উচ্চসীমা ঘণ্টায় বিশ মাইল, একটু দূরে গেলে তিরিশ। মোটরওয়েতে ৭০ মাইল ( ১১২ কিমি ) গতি অনুমোদিত । সেখানে কদিন যাই ? যেখানে আমার নিত্যিদিনের ঘোরাঘুরি - হাটে বাজারে , বন্ধু সন্দর্শনে, তসেখানে আমার গাড়ির টিকিটি বাঁধা আছে তিরিশ বা বড়জোর পঞ্চাশ মাইল বেগে । প্রয়াত ভাস্করদার ( ভাস্কর দত্ত , সুনীলদার অভিন্ন হৃদয় বন্ধু) পুত্র অর্ণবের বাড়ি থেকে কিছু সঞ্চিত বই সংগ্রহের জন্য উত্তর লন্ডনের স্টোক নিউইংটন গেলাম গত রবিবার - এককালের সেই বিখ্যাত ওয়েস্টওয়ে আকীর্ণ হয়ে আছে অজস্র ক্যামেরায়, ওয়েম্বলি, হ্যামারস্মিথ থেকে কিংস ক্রস ছাড়িয়ে গাড়ি চলে ধীরে মন্দ গতিতে, আইন বাঁচিয়ে । তাহলে এত ফাস্ট গাড়ি আমার কোন কাজে লাগে ?জানি রথ চালকের অন্তবিহীন স্বাধীনতা আছে এক দেশে - কিছু নির্ধারিত এলাকা বাদে মোটরওয়েতে গাড়ি চালানোর গতির কোন উচ্চসীমা বাঁধা নেই , শুমাখার বা লুইস হ্যামিলটনের মতন যেখানে যেমন খুশি যে কোন স্পিডে হারিয়ে যেতে পারি । লুইবেক থেকে হামবুর্গের অত্যন্ত সমতল পথে ঘণ্টায় অনায়াসে দুশো কিলোমিটার গতিতে পৌঁছে মনে হয়েছে মাটি ছাড়ালেই তো প্লেন ! গতি আরেকটু বাড়ালেই হয়ে যাবো জন গ্লেন । কিন্তু নিত্যদিনের কাজের জগতে জার্মানিতেও তো আবার সেই ৩০/৫০ কিলোমিটারের শিকলি পরানো আছে।আজ মনে পড়ে আমাদের প্রতিদিনের পথের ধুলায় সঙ্গী এক যান – গ্রামের কাঁকর বিছানো পথে , গরুর গাড়ি চলে চলে দু পাশে গভীর গর্ত মাঝখানে জেগে থাকা মাটির চরের সঙ্গে সমঝোতা করে , ছাগল গরু সাইকেলকে পাশ কাটিয়ে রাস্তায় শুকোতে দেওয়া ধানের ওপরে চলে যায় গাড়ি। সিঁথি বরানগরের অলিতে গলিতে ভেঁপু বাজিয়ে পথচারীকে জানায় আমি পেছনে আছি । উচ্চ গতির অহেতুক অহংকার ছিল না তার, হাটখোলা থেকে কলুটোলা, পদুমা গ্রাম থেকে কেন্দুলির মেলা ঠিক পৌঁছে দিয়েছে সে , তার নিজস্ব চালে। পথে হলো দেরি ? হোক না । দের আয়ে পর দুরুস্ত আয়ে ।ততক্ষণ সিট বেল্ট বর্জিত আরামদায়ক গদিতে গা এলিয়ে দিয়ে বসে দুটো গল্প গাছা , পথচারী নিরীক্ষণ । দাও ফিরে সে অ্যামবাসাডার , লহ এ জাগুয়ার ! গতি সম্পর্কিত কবিতা -তুষার রায় এই ভাবেই তো গরুর গাড়ির গতি বাড়ালেই মোটর আবার মোটর থেকে মাটি ছাড়ালেই প্লেন আরো গতি বাড়ালে জন গ্লেন , পারে অভিকর্ষের বাইরে চলে যেতেদিলদার নগর ৪ - Aditi Dasgupta | ঘটমান বর্তমান ঘটেনাতো পিছনের কথামুখ ভুলি।দিলদরিয়াতে নেমে একে একে খুলে যায় --এ ‘আমির’ আবরণ গুলি।।এ শহরে গরম বড়ো শুকনো। বেলা না বাড়তেই লাল ধুলোয় ঘূর্ণি বাতাস উড়িয়ে নিয়ে যায় শুকনো শাল পিয়াশাল এর পাতা। পথের মানুষগুলির শরীর থেকে শুষে নেয় জল ---মুখ আর হাত পায়ের আঙ্গুলগুলি শুকিয়ে ওঠে। ঠোঁট, গাল ফেটে যায় শীতকালের মতোই। ভিজে গামছা মুখে মাথায় জড়িয়ে লোকে কাজে কম্মে বেরোয়। কোর্ট কাছারি ইস্কুল শুরু হয় বেশ সকাল সকাল, বেলি, জুঁই আর পাকা কাজুফলের গন্ধ মেখে। কিন্তু ছুটির সময়তো সেই পুড়তেই হয়! রিকশা করে মাইক নিয়ে ঘোষণা করা হয় বাড়ি থেকে না বেরুতে। এদিকে শুক্রবার শুক্রবার বই বদলায় আর সেটাও জানাতে মাইক নিয়ে ভর দুপুরে বেরোয় শহরের বিখ্যাত ঘোষক সাব্বির। পরিচিত দানাদার, একটু বিকৃত নাটুকে গলায়, জগাখিচুড়ি হিন্দি তে প্রতিধ্বনি হতে থাকে ---হাঁ.....আইয়ে… অব মিলনী টকিস কি রূপলি পরদে মে দে….খিয়ে…… মস…হুর ফিল্ম…. খুদা গাওয়া…. আআআ…..। বাতাসে ঘুরপাক খেতে খেতে ঘরের কোনে পৌঁছে যায় সেই আওয়াজ। শুধুই পেটের দায়, নাকি মনের মাঝের অন্য ভুবন থেকেও আসে এই জোর? আমাদের একেকজনার থাকা কি কেবল একটি মাত্রাতেই, একটি ভুবনেই বাঁধা ? মুরগি বেচা আতাউর সন্ধ্যে গড়ালে দোকানের ধোয়াধুয়ি শেষে সবজিবাজারের দিকটার খালি চাতালে বসে বাঁশি বাজায়। পাশেই তাসের আড্ডা বসে। ওজনে দাঁড়িমারা মাছওয়ালা স্বপন তাসের দিকে নজর রেখে মাথা দোলায়। জামিলা পাগলী তার সুঠাম শরীর নিয়ে এখানেই রাতে ঘুমোয় । অনেক রাতে দু একটা ছায়া ঘোরে আশেপাশে, আর তাদের ঘিরে চেঁচামেচি করে ঘুরতে থাকে খান তিন চার নেড়ি কুকুর । এরা দিনের বেলা জামিলার সাথেই খায়। নেপালি নাইট গার্ড মস্ত বড় টর্চ নিয়ে এসে দাঁড়ায়। সবাই তাকে বাহাদুর বলে ডাকে।অন্ধকারে পাশের অশ্বত্থ গাছ বুঝি সব দেখে, আর দেখে মধুশালা ফেরত কিছু রসিক জন, নাইট শো ভাঙা নারী পুরুষ। দুপুরের পর থেকেই ঘরের দেওয়ালগুলি ভিতরে তাপ ছাড়তে শুরু করে। দরজা জানলা বন্ধ করে ঘর অন্ধকার করে যে আরামটুকু নিয়ে কিছুটা সময় কাটানো গেছে, আর সেটি থাকেনা। রাত পর্যন্ত ঘরগুলি তে ঢুকতেই ইচ্ছা হয়না। তাই বিকেল থেকে সন্ধ্যে, সন্ধ্যে থেকে রাত লোকজন রাস্তায়, ছাদে, মাঠে। রান্নাবান্নাও আর রাতে তেমন করতে চায়না কেউ। ও বেলার ভাতে জল ঢেলে, হয়ত সামান্য ভাজাভুজি। ছাদেই বিছানা পাতে বহু মানুষ। গ্রীষ্ম যাপন তাই একা নয়,আশপাশের মানুষকে নিয়ে খোলা আকাশের নিচে--- চাঁদের আলোয় বা তারার আলোয় ---কেমন জানি এক বয়ে যাওয়া গল্প। এক ঝলক ঠান্ডা হাওয়া বা ভেসে আসা কোনো সুর, ঘরোয়া সাদামাঠা কথা, অজানা আদেখা তীর্থস্থানের গল্প গুনগুন করে বলে যায় কেউ। তাকে ঘিরে কৌতূহল। কখনো বা অতীতে ঘটে যাওয়া কোনো দুঃখের চারণ, এ জীবনে, কারবালা,বা মহাভারতের পাতায় অভিমন্যু ----সব একাকার হয়ে যায় এই সব রাতে, রাতের গল্পে। গাছের পাতাগুলি শিরশির করে যেন মাথা নাড়ে। সব দেশে সব কালে সাধারণ মানুষ বুঝি এভাবেই একসাথে বলে যায়, সয়ে যায়, নিয়ে যায় গল্পের পিছনে গল্পকে। আর আমাদের দিলদার নগর তো গল্প বলে সারা অঙ্গ দিয়ে।ওরাও গল্প করছিলো। দীর্ঘ পরীক্ষা শেষে সারাদিন কী করি কী করি অস্থিরতায় অপেক্ষা করে থাকে বিকেলের জন্যে। শহরের মধ্যিখানে বিশাল সেই মাঠ। দূর থেকে হেঁটে আসা মানুষটিকে যেন পুতুলটির মতো লাগে, ঠাহরই হয়না ঠিক ঠাক। কাছে এলে তবে বোঝা যায়। এ মাঠে গরমে ফুটবল, শীতে ক্রিকেট, সকালে বিকালে দেহচর্চা, বয়স্কদের হাঁটা। কলেজ আর ইস্কুলের মাঠ একসাথে, তাদের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতাও হয়, আর হয় ২৬ জানুয়ারি র দশ মাইল দৌড়। বেলুন, ফানুস, লোকের ভিড়ে জামজমাট। সাইকেল চালানো শেখে ছেলেমেয়েরা। ওদেরও কেউ কেউ এখানে সাইকেল শিখেছে, যারা শেখেনি তাদের শেখাচ্ছে। কানের পাশ দিয়ে বাতাসের শব্দ বয়ে যায়, জোরে দৌড়ালে বা সাইকেল চালালে।একটু আগেই আলো ছিল। তখন পর্যন্ত ট্রেনিং চলেছে। পিছনে তেঁতুল গাছ আর কলেজ হোস্টেলের আড়ালে পশ্চিম সূর্য একটু লালচে হতেই সামনে পূব দিকে দূ..উ... রে…রাস্তার ওপারে কলেজ আর কলেজিয়েট ইস্কুলের হলদে মেরুন পুরোনো বাড়িগুলো কেমন জানি একটা কমলারঙা হয়ে গেলো। রাস্তা দিয়ে সাইকেল, গাড়ি, মানুষজন সবই ছোট ছোট দেখায় এখান থেকে। ওরা যেন কেমন আলাদা একটা দ্বীপে বসে আছে। ডান দিকে কাঁচা রাস্তার ওধারে পুরাতন জেলখানার জানালাগুলি এখন মাটি ছোঁয়া, টিমটিমে আলো দেখা যায় দু একটিতে। ওধারে একদিকে ভবঘুরেদের আবাস হয়েছে, এদিকটাতে কিছু মানুষ থাকে, একটু ছান্নছাড়া যেন। এরা ঠিক জানেনা ওরা কারা। কতদিনের এই জেলখানা কেউই ঠিক বলতে পারেনা। ইংরেজদের আগে থেকেই এটা ছিল। ছোট থেকে শুনে আসছে একটা নাকি সুড়ঙ্গ আছে ভিতরে, সেই পশ্চিম দিকে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পাহাড়ের গড়ে গিয়ে উঠেছে। ওদিকে হাতির আনাগোনা।পাঠান, মোগল, বর্গী, নাকি জেলের কয়েদি বানিয়েছিলো সেই পথ তাও কেউ সঠিক বলতে পারেনা। এই জেলখানা নাকি আসলে দূর্গ। কখনো পাঠান, কখনো বর্গী আবার কখনো এখানে ডেরা বেঁধেছিলো আলিবর্দি নবাব, নাতি সিরাজ, সেনাপতি মীর জাফর! ইস্কুলের ইতিহাস বইতে সেসব কথা লেখা নেই । মুর্শিদাবাদ, ঢাকা, দিল্লী, বোম্বাই, কলকাতার কথা মুখস্ত করেছে ওরা, আর ঘর করেছে এসব নিয়ে। ঘরের গল্প মুখে মুখেই ফিরেছে খুব বুড়ো মানুষ, শহরে পড়ে থাকা তন্নিষ্ঠ অথচ অস্বীকৃত মানুষজনের আড্ডায়। মাঠ এখন যত বড়, তার চেয়ে অনেক বড়ো ছিল নাকি আগে। ইস্কুল, কলেজ, পোস্টাপিস, হাসপাতাল--- কিচ্ছু ছিলোনাক সেই তেপান্ন্তরে! এ মাঠ যুদ্ধের মাঠ। পাঠানের সাথে মোগল, বর্গীর সাথে নবাবের যুদ্ধের মাঠ। মাটি ছুঁয়ে বাস করা মানুষের কত বিদ্রোহের সাক্ষী! ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, জনতার সামনে ফাঁসিও দেখেছে এই মাঠ! আর ওই যে দূরে ইস্কুলের কোয়ার্টার, সেখানেই তো বাস করতেন এক ঋষি মানুষ। নব জাগরনের রাজনারায়ণ। শহরের লাল মাটির চওড়া রাস্তাগুলি, শহরের পাশের পাহাড়, জঙ্গল, ঝর্ণা ----সব কিছুকে ভালোবেসে তিনি চেয়েছিলেন এই নগরের নাগরিক হিসাবেই পরিচিতি পেতে। মেয়ের বিয়ে দিলেন এখান থেকেই। সেই মেয়ের সন্তান নাতিটি বিলাত গেলেও বিলাতি হলোনা, নিজেকে দিয়ে দিলে দেশের কাজে। সশস্ত্র ছিল সেই পথ, আর সেই পথই আবার তাকে টেনে আনলে এই শহরেই। অনেক পরে তার পথ গিয়ে ছোঁবে তারার আলোয় মাখা সর্ব মানুষের মুক্তির পথকে, সে নিজেও হয়ে যাবে আরেক ঋষি, লিখবে, দিব্য জীবন ! অথচ এই শহর ই দেখো কত কতবার নরক দর্শন করলো! নাকি সে সেই কষ্টের মধ্যে দিয়েই বীতশোক হওয়ার পথে এগোলো? পূর্ণিমার পর পর ই চাঁদের ক্ষয় শুরু হয়। শিবাজী সদাশিব এর গল্পে গড়া মন সহ্য করতে পারেনা বর্গীর নিষ্ঠুরতার গল্প । আবার সেই নাগপুর থেকে! যেখানে কত আত্মীয়, আসাযাওয়া, ঝলমলে স্বাধীন জীবনের হাতছানি! এ শহরের রেল স্টেশনকে একদা বেঙ্গল নাগপুর রেল স্টেশন বলেতো ডাকা হত! বীর শিবাজীর গেরুয়া ঝান্ডা দুর্বলের রক্ষাকারী, শত্রুর যম। নারী তাঁর কাছে পরম সম্মানের, যে ধর্মেরই হোন। তাহলে তাঁর পথের রেখা কাজে লাগিয়ে কারা চড়াও হলো এ শহরে? তাদের ওড়ানো ধূলিটুকুই শুধু গেরুয়া, আর সব কালো, মাথার লাল ফেট্টি টুকু বাদ দিয়ে! সারা বাংলা জুড়ে ওলোট পালট এই হিংস্র বুলবুলির দাপটে! তোলাবাজি আর অত্যাচারের সেই ঝড় দিলদারকে রক্তে ভিজিয়ে দিয়ে গেলো। অথচ দেখো, বৃন্দাবনকে অনুসরণ করে গড়ে ওঠা কিছুদূরের পরম বৈষ্ণব সহরটি কিন্তু বেশ লড়াই দিয়েছিলো। তাদের নগর দেবতাই নাকি স্বয়ং বর্গীর দল মর্দন করে দিলেন বিশাল কালো কুচকুচে কামানটি দেগে । দিলদারে কামান ছিলোনা, ছিল দেবালয়, মাজার, মসজিদ। লোকে বলে কাবার চেয়ে নাকি মাত্র এক তিল কম তার মান। সেখানেই মানহারা হলো মানবী! যে অমৃত সুধার ভরসায় মানব শিশু চোখ খোলার আগে মুখ খোলে, খেলার ছলে তারোয়ালের কোপে সেই অমৃত ভান্ডার ছিন্ন করলে তারা! গলায় দড়ি বেঁধে পশুর মতো ধরে নিয়ে যাওয়া হলো বধূ কন্যা , একে একে ছিন্ন ভিন্ন করা হলো তাদের সতীপীঠ ----হর হর মহাদেব চিৎকারে! নাক কান কাটা পুরুষ গুলি হাহাকার করে বেড়াতে লাগলো পুড়ে যাওয়া ঘরবাড়ি খেত খামারে! বারবার আসতো তারা ---এক দশকেরও বেশী সময় ধরে! বাংলার জলময় দক্ষিণ দিক নাপসন্দ ছিল শুকনো জায়গার এই হানাদারদের। সেই দিকটি নাহয় জলদস্যুদেরই থাক। দিলদার তাই অন্তত বেঁচে গেলো মগ, পর্তুগীজ, আরাকানির হাত থেকে কিছুটা। তবু খবর তো আসে কিছু! আত্মীয় স্বজন আসা যাওয়ায়! রাধামানির দাস বাজার আর কদ্দুর! বুলবুলির দল এলো উত্তর পশ্চিমের পঞ্চকোট পাহাড়ের পথ ধরে পুরুলিয়া হয়ে বর্ধমান জ্বালিয়ে বাঁকুড়া হয়ে। তাদের দমনে আলিবর্দি মীর জাফর সিরাজ। বার বার যুদ্ধ বার বার আক্রমণ। রাজায় রাজায় লোভের যুদ্ধে তস্করের পোয়া বারো! পালের গোদা ভাস্কর পন্ডিতকে ছলে বলে আলিবর্দি মুর্শিদাবাদ নিয়ে গিয়ে হত্যা করলে আক্রমণ হলো আরো তীব্র আরো নিষ্টুর-- রঘুজী ভোসলে র জমানায়। ছারখার শহর শেষমেষ বুঝি একটু শান্ত হলো কোম্পানি ফৌজ এর হাতে পড়ে। তখন কে জানতো যে, সেই আপাতত শান্তি আসলে আরেক নৈরাজ্যের সূচনা? তিলে তিলে ভাতে মারার অদ্ভুত এক বেনিয়া জমানার খুঁটি পুজো? ওরা চুপচাপ বসে আছে। গল্প টা বলেছিলো ইতিহাসের পাগলা স্যার। কোনো ইস্কুলে পড়ায়না , অথচ কোচিং এ কি ভীড়! গল্প বলে বলে মাথায় ঢুকিয়ে দেয় । ফাঁকিবাজরা গল্পটুকু লিখেই পাস নম্বর তুলে ফেলতে পারে। গল্প তো আর ভোলেনা তারা, সেতো হৃদয়ে গাঁথা! ক্লাসের পড়ার বাইরে সব কথা ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি ওরা, তবু আবছা মত কিছু কথা, যা এমনি বলা কওয়ায় আসেনা, অথচ রোজকার জীবনে, পড়ে আসা ক্লাসের পড়ার সাথে কী যেন একটা ভাবে জড়িয়ে পড়ে। কত বই স্যারের! কিছু বই একটু অন্যরকম,ওগুলোকে জার্নাল বলে। বিদেশ এর গন্ধমাখা কিছু। আবার খুব পুরোনো, কেমন যেন বাংলা, ছাপাটাও অন্য রকম। প্রকাশনা তারিখ দেখতে শিখেছে ওরা –প্রায় একশ বছর আগের! আদর করে ওরা পাগলা বলে, আসল নাম তো মদনমোহন! পুরো নামে ডাকেনা কেউ। মা ছাড়াও স্যারের বৌ কে দু একবার দেখেছে ওরা, বাপের বাড়ি থাকে। বর্গীদের সবাই নাকি মারাঠা ছিলোনা! একদিকে তারা যেমন দস্যু লেঠেল পুষতো, অন্য দিকে যত রাজ্যের অপরাধী, চালচুলোহীন অপদার্থ, জাল- জুয়াচোর গিয়ে আশ্রয় নিতো বর্গী শিবিরে --- লাভের গুড় খেতে। একটা দেশ, জাতি বা আদর্শ ---তিল তিল করে গড়ে উঠতে, শিখরে পৌঁছতে কতইনা তার সংগ্রাম! আর দেখো যখন তার কাঠামো,আদর্শ দুর্বল হয় তখন কেমন মাছির মত চারপাশ থেকে ছুটে এসে ঢুকে পড়ে একেবারে উল্টো পথের মানুষ! নাকি আবর্জনা? দারিদ্র তাদের শুধু অর্থে নয়, সর্বার্থে ---পরমার্থে ! স্যার মাথা নেড়ে ছড়া কাটেন :সর্বহারা নয় এরা সর্বার্থে হারা।বীর্যহীন মেধাহীন পাজি হতচ্ছাড়া।। সমাজের চাকা নয়, পুতিগন্ধ ডোবা! সমাজকে করে দেয় নীতিহীন বোবা।।রাজা ধর্মহীন হলে মাৎস ন্যায় দেশে । এদের উত্থান হয় গরীবের বেশে।।সার্বিক অনুকম্পা আহরণ করে ।চিত্তের বিকারেতে দশ দিক ভরে।।লুন্ঠন, জালিয়াতি করে ভরে পেট।ইতিহাসে লুম্পেন প্রলেতারিয়েট।।এটা সেটা ছাড়া ছাড়া গল্প সল্পের মধ্যে জেলখানার আলো….অন্ধকার পথ বেয়ে ওরা কি চলে গিয়েছিলো ১৭৪০ থেকেশুরু হওয়া সেই জ্বালা পোড়া সময়টাতে? মাথার উপর আচমকা পেঁচার ডাক,একটু মেঘের গুড় গুড়, এক ঝলক ঠান্ডা হাওয়ায় ভর করে বড়ো কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি। তড়বড় করে উঠে পড়ে সব।বৃষ্টি নামে ঝমঝম করে । নাকে এসে লাগে গরম মাটিতে প্রথম বর্ষার জল খাওয়া ভাপ আর সুগন্ধ। কিন্তু এখন রাত্রি নামছে। ঘোর অন্ধকারে এবড়ো খেবড়ো মাঠের মধ্যে দিয়েই ওরা সাইকেল চালাতে থাকে দূরে আলো জ্বালা রাস্তার দিকে। প্রত্যেকেই এখন পৌঁছতে চায় যার যার বাড়ি, যত তাড়াতাড়ি। আলো জ্বলা বাড়ির স্থিতিশীল বর্তমান শুষে নেয় কত অজানা ভয়, কত অনিশ্চয়তা! ওরা এখনো বোঝেনি এরকম প্রতিটি বর্তমান আর বর্তমান এর প্রতিটি আলোজ্বলা বাড়িই একদিন সময়ের আবর্তে হারিয়ে যায়। নাকি কিছুই হারায়না ? দিলদার তার বুকের মধ্যে তাদের টেনে নেয় মাত্র? তারপর তারা হয়ে যায় গল্প –উপকথা, কোনো শোকগাথা হয়তো বা, রূপকথাও কখনো কখনো ---উপাদানের চরিত্র মাফিক?কিষেণজি মৃত্যু রহস্য - পর্ব ১৩ - বিতনু চট্টোপাধ্যায় | কিন্তু সেদিন, ২০০৮ সালের ২রা নভেম্বর শালবনিতে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, রামবিলাস পাসোয়ানের কনভয়ে বিস্ফোরণের পর পশ্চিম মেদিনীপুরের পুলিস সুপার রাজেশ কুমার সিংহ কেন প্রথমে জানিয়েছিলেন, বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে পড়ে পুলিশের গাড়ি উল্টেছে? ঠিক কী ঘটেছিল সেদিন তা হুবহু লিখব এক অফিসারের মুখে, যা তিনি আমাকে পরে বলেছিলেন। তিনি সেদিন ছিলেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের কনভয়ে।‘সেদিন অনুষ্ঠান শেষ হয়ে যাওয়ার পর প্রথমে বেরিয়ে যাওয়ার কথা ছিল রামবিলাস পাসোয়ানের। তারপর মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের। এমনই প্ল্যানিং করা ছিল জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে। সম্ভবত মাওয়িস্টদের কাছেও এই খবর ছিল। কিন্তু সেদিন অনুষ্ঠান শেষের পর বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর আগে বেরিয়ে যান। মঞ্চের পিছনেই চা খাওয়ার বন্দোবস্ত ছিল। অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর সমস্ত ভিআইপি যান সেখানে। সেখানে সজ্জন জিন্দল অতিথিদের কিছু খেয়ে যেতে বলেন। কিন্তু চিফ মিনিস্টার শুধু চা খেয়ে বেরিয়ে যান মেদিনীপুর সার্কিট হাউসের উদ্দেশে। রামবিলাস পাসোয়ান কিছুক্ষণ বসে যান। তিনি বেরোন মিনিট দশেক বাদে। মাওয়িস্টরা ব্লাস্টটা করাতে চেয়েছিল বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের কনভয়ে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীই ছিলেন টার্গেট। ওরা হয়তো দূর থেকে নজরও রাখছিল রাস্তার কনভয়ের দিকে। কিন্তু কোন কনভয়ে কে রয়েছেন সেটা দূর থেকে বোঝা সম্ভব ছিল না। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের কনভয়কে ওরা রামবিলাস পাসোয়ানের ভেবে ভুল করে। চিফ মিনিস্টার বেরনোর কিছুক্ষণ পর রামবিলাস পাসোয়ান বেরোন শালবনি থেকে। আর তার কনভয়েই ডিরেকশনাল ল্যান্ডমাইন ব্লাস্ট করায় মাওয়িস্টরা। ঠিক যে মুহূর্তে ব্লাস্ট হয় তখন চিফ মিনিস্টারের গাড়ি মেদিনীপুর সার্কিট হাউসে ঢুকছে। চোখের সামনে ব্লাস্ট দেখে গাড়ি থেকেই চিফ মিনিস্টারকে ফোন করেন রামবিলাস পাসোয়ান। চিফ মিনিস্টার সার্কিট হাউসে গাড়ি থেকে নেমে সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাটা বলেন তাঁর নিরাপত্তা উপদেষ্টা অরবিন্দ কুমার মালিওয়ালকে। চিফ মিনিস্টারের ঠিক আগেই ছিল জেলার পুলিশ সুপার রাজেশকুমার সিংহের গাড়ি। হাতের সামনে পেয়ে অরবিন্দ মালিওয়াল ব্লাস্টের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন এসপিকে। সার্কিট হাউসের ভেতরে না ঢুকে চিফ মিনিস্টার তখন দাঁড়িয়ে আছেন গাড়ির সামনে। তাঁর কয়েক ফুট দূরে দাঁড়িয়ে আছি আমি। এসপি দেখলাম, কাউকে একটা ব্যস্ত হয়ে ফোন করছেন। ঠিক সেই সময় সার্কিট হাউসে এসে পৌঁছোলেন মেদিনীপুর রেঞ্জের ডিআইজি প্রভীণ কুমার। ডিআইজির গাড়ি ছিল চিফ মিনিস্টারের কনভয়ের একদম শেষে। এসপিকে কারও সঙ্গে কথা বলতে ব্যস্ত দেখে মালিওয়াল বিষয়টা দেখতে বলেন ডিআইজিকে। ডিআইজিও ফোন করেন কাউকে। অস্থিরভাবে এদিক-ওদিক দেখছেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। মালিওয়ালেরও এক অবস্থা। দু’জনেই তাকিয়ে রয়েছেন এসপি এবং ডিআইজির দিকে। আর দু’জন অফিসারই ফোনে কথা বলছেন। মিনিট খানেক বাদে এসপি ফোন ছেড়ে বললেন, ‘‘কিছু হয়নি তেমন। ইলেকট্রিকের তার ছিঁড়ে পড়েছে কনভয়ে পুলিশের গাড়ির ওপর। তাতেই টাল সামলাতে না পেরে পুলিশের গাড়ি রাস্তার ধারে পড়ে গিয়েছে।’’ এসপির কথায় আশ্বস্ত হন চিফ মিনিস্টার। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফোন ছেড়ে প্রভীণ কুমার জানালেন, ‘‘স্যার, ব্লাস্ট হয়েছে। ব্লাস্টে ইলেকট্রিক তার ছিঁড়ে মাটিতে পড়েছে। জোরে আওয়াজ হয়েছে, বড় ব্লাস্ট ছাড়া তা হতে পারে না।’’২রা নভেম্বর, ২০০৮। এই ঘটনার ঠিক পরেই শুরু হয়ে গেল লালগড় আন্দোলন। ঠিকঠাক ধরলে আন্দোলনটা শুরু হল ৮-৯ তারিখ থেকে। ২ তারিখের ঘটনার বিহ্বলতা কাটতে জেলা এবং রাজ্য পুলিশের লেগে গেল কম-বেশি চব্বিশ ঘন্টা। ৪-৫ নভেম্বর থেকে শালবনি, লালগড়ে শুরু হল পুলিশের জোরদার তল্লাশি অভিযান। মুখ্যমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কনভয়ে ব্লাস্টের মতো বড় ঘটনা ঘটেছে, পুলিশের ওপর চাপও ছিল যথেষ্ট। লালগড়ের কাঁটাপাহাড়ি, বড়পেলিয়া এলাকা থেকে কয়েকজন গ্রামবাসীকে গ্রেফতার করল পুলিশ। আর এই গ্রেফতার করতে গিয়ে মহিলা, বাচ্চাদের ওপর হল লাঠিচার্জ, মারধোর। নিরীহ মানুষের ওপর পুলিশি অত্যাচারের অভিযোগকে সামনে রেখেই লালগড় এবং তাকে কেন্দ্র করে এক বিস্তীর্ণ জায়গায় মাওবাদীদের নেতৃত্বে গ্রামবাসীরা শুরু করল সরকার বিরোধী বেপরোয়া আন্দোলন। যার পরতে পরতে রয়েছে হিংসা-প্রতিহিংসা, খুনোখুনি, রাজনৈতিক লড়াই। যে আন্দোলন চলল কার্যত ২০১১ সালের ১৩ই মে পর্যন্ত। আর রাজনৈতিক মেরুকরণের পীঠস্থান এপার বাংলার একটা বাচ্চাও জানে, ওইদিন মানে ১৩ই মে ২০১১, নিরবচ্ছিন্ন ৩৪ বছরের সিপিআইএম পরিচালিত সরকারের ডেথ সার্টিফিকেটে গণসাক্ষর করলেন রাজ্যের মানুষ। তার সাতদিন বাদে ২০ মে সরকার গঠন করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ১১ই নভেম্বর, ২০০৮ আগের দিন সন্ধ্যায় খেজুরি থেকে বেরিয়ে ঝাড়গ্রাম শহরে ঢুকতে ঢুকতে হয়ে গিয়েছিল রাত প্রায় বারোটা। মধ্যরাতে ঝাড়গ্রামের অরণ্য সুন্দরী হোটেলে গিয়ে উঠলাম। ২০০৬ সালের গোড়াতেও এই হোটেলে ছিলাম বেশ কয়েকদিন। ঝাড়গ্রাম জেল লাগোয়া অরণ্য সুন্দরী হোটেল থেকে বাস স্ট্যান্ড এবং স্টেশন ঠিক পাঁচ মিনিটের হাঁটা রাস্তা। ১১ তারিখ একদম সকাল সকাল স্টার আনন্দের ঝাড়গ্রামের সাংবাদিক অমিতাভ রথকে ডাকলাম হোটেলে। আগের দিনই বলে রেখেছিলাম। লালগড় যাব। আগে কোনওদিন যাইনি, রাস্তা চিনি না। অমিতাভকে দরকার। সকাল আটটা নাগাদ মোটরসাইকেল চালিয়ে অমিতাভ এল এক জবরদস্ত দুঃসংবাদ নিয়ে। ‘দাদা, গতকাল বিকেল থেকে লালগড়ে ঢোকার বিভিন্ন রাস্তা কেটে দিয়েছে গ্রামবাসীরা। পুলিশকে ঢুকতে দেবে না বলে গাছ ফেলে সব রাস্তা অবরোধ করেছে। গাড়ি করে তো লালগড় যাওয়া যাবে না।’‘যত দূর গাড়ি করে যাওয়া যায় যাব, বাকিটা যাব মোটরসাইকেলে। তোমার মোটরসাইকেলে তেল আছে?’নন্দীগ্রামের অভিজ্ঞতা ততদিনে শিখিয়েছে, যে কোনও আন্দোলনের উৎপত্তিস্থলে যাওয়ার সেরা বাহন মোটরসাইকেল। কাটা রাস্তা দিয়ে যাওয়া তো সহজ বটেই, আচমকা বিপদে-টিপদে পড়লে পালানোও সহজ। ‘না তেল নিতে হবে।’রওনা দিলাম ঝাড়গ্রাম শহর থেকে। রেল লাইন পেরিয়ে এগোচ্ছি। মোটরসাইকেল চালাচ্ছে ঝাড়গ্রামের স্টার আনন্দর সাংবাদিক অমিতাভ রথ, লালগড় আন্দোলনে প্রবেশে আমার প্রথম গাইড। পেছনে গাড়িতে বসে উজ্জ্বল আর আমি। পেট্রল পাম্প থেকে মোটরসাইকেলে তেল ভরা হল। মিনিট পনেরোর মধ্যে পৌঁছে গেলাম দহিজুড়ি মোড়ে। রাস্তায় ভর্তি লোক।দহিজুড়ি মোড় থেকে ডানদিকে কোণাকুণি একটা রাস্তা চলে গিয়েছে। সেই রাস্তা ধরলাম আমরা। থামল অমিতাভ, আমরাও গাড়ি থামালাম। নামলাম গাড়ি থেকে। গাড়ি থাকবে দহিজুড়িতে। আমি আর উজ্জ্বল উঠে বসলাম অমিতাভর মোটরসাইকেলের পিছনে। অমিতাভরই পরামর্শে। কখন কোথায় রাস্তা কাটা ঠিক নেই। গাড়ি রেখে মোটরসাইকেলে যাওয়াই ভাল। তাছাড়া গ্রামে কিংবা মফস্বলে মোটরসাইকেলে তিনজন স্বভাবিক দৃশ্য। মোটরসাইকেলে চেপে যাচ্ছি আর ভাবছি লালগড়ে পৌঁছে কী স্টোরি করব তা নিয়ে। মাঝে মাঝে অমিতাভকে জিজ্ঞেস করছি লালগড় নিয়ে। কিন্তু এত হাওয়া, প্রায় কোনও কথাই শোনা যায় না। আধ ঘন্টাখানেক পর মোটরসাইকেল থামাল অমিতাভ। ‘দাদা, নদী পেরোতে হবে।’ নদীর ওপারে লালগড়। দু’দিকে চওড়া বালির চরা। মাঝখানে ফুট পঞ্চাশেক চওড়া কাঁসাই নদী। কিছুটা বেশি কিংবা সামান্য কমও হতে পারে। ভূগোল বইয়ে এই নদীর নাম কংসাবতী। লোকাল নাম কাঁসাই। এমনিতেই রুক্ষ জায়গা ঝাড়গ্রাম। তার মধ্যে বর্ষা গিয়েছে সবে মাস দুয়েক আগে। তাই কাঁসাইয়ে তবু জল আছে কিছু। ফেব্রুয়ারি, মার্চ মাসে তো গিয়ে দেখেছি লোকে ওই জায়গা দিয়ে সাইকেল চালিয়ে কাঁসাই পেরোয়। এখন নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহ, জলের গভীরতা এক থেকে দেড়-দু’ফুটের মধ্যে। কিন্তু পরিষ্কার ঝকঝকে জল। হাঁটু পর্যন্ত প্যান্ট গুটিয়ে নিলাম তিনজনেই। জুতো খুলে বেঁধে নিলাম মোটরসাইকেলের কেরিয়ারে। তারপর খালি পায়ে কাঁসাই নদী পেরিয়ে গেলাম আমরা। উজ্জ্বলের হাতে ক্যামেরা, মাইক। আমি আর অমিতাভ ঠেলে নিয়ে গেলাম মোটরসাইকেল। দু’জন মিলে মোটরসাইকেল ঠেলে নদী পেরোতে তেমন কষ্ট হয়নি, কিন্তু কত ধানে কত চাল বোঝা গেল চরার বালি পেরনোর সময়। রাস্তায় গিয়ে উঠে টানা পাঁচ মিনিট রেস্ট। আবার উঠে বসলাম মোটরসাইকেলে। মিনিট চল্লিশেক পর লালগড় থানা। প্রায় সাড়ে দশটা বাজে। লালগড় থানা, সিদু সোরেন এবং দাবি সনদ ২০০৯ সালের প্রায় গোড়া থেকেই পুলিশের হিট লিস্টে উঠে এসেছিল সিদু সোরেনের নাম। আমি সিদুকে প্রথম দেখি ২০০৮ সালের ১১ই নভেম্বর। যেদিন প্রথম লালগড় থানার সামনে পৌঁছেছিলাম সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ। লম্বা, পেটানো চেহারা। থানার সামনে রাস্তায় বসে সাদা কাগজে লাল আলতা দিয়ে দাবি সনদ লিখছে এক যুবক। পাশে সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি পরা মাঝবয়সী এক ব্যক্তি সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। পরে জেনেছিলাম, তাঁর নাম লালমোহন টুডু। লালমোহন টুডু বলছেন কী লিখতে হবে, গোটা গোটা অক্ষরে লিখছে সিদু। ছেলেটাকে কোনওদিন আপনি বলিনি, এত কম বয়েস। তাই লেখাতেও আর আপনি সম্বোধন করছি না। সেদিন দেখেছিলাম ঝকঝকে দুটো চোখ। এমন চিবুক, কাঁধ এবং চোখ সচরাচর এই এলাকার কম বয়সী ছেলেদের হয় না। সিদুর চোখ এবং চেহারার গড়ন বলে দিচ্ছে, এই ছেলেটাই লিডার। কয়েক মাসের মধ্যেই চেহারা আরও পালটে গেল ছেলেটার। আরও শক্ত হল চোয়াল। হিংস্রতা এল চোখে-মুখে। ২০০৯ সালের লোকসভা ভোটের ঠিক আগে শেষ দেখা হয়েছিল সিদুর সঙ্গে। তখন ওরই নিরাপত্তায় বেশ কিছু যুবক। সিদুরও বয়েস ওই সাত মাসেই বেড়ে গিয়েছে কয়েক বছর। হাতের বন্দুক ওই কয়েক মাসেই তাকে দিয়েছে বেপরোয়া কাঠিন্য এবং আত্মবিশ্বাস। দশ-বিশ বছর ধরে চেনা তার গ্রামের লোকও চমকে উঠেছে সিদুর হঠাৎ তৈরি হওয়া ব্যক্তিত্ব দেখে। ১১ই নভেম্বর ২০০৮, আমরা যে কয়েকজন সাংবাদিক লালগড় থানার সামনে হাজির হয়েছিলাম, তাদের সবার মোবাইল ফোন নম্বর লিখে নিচ্ছিল সিদু নিজে। তখন দুপুর বারোটার এদিক-ওদিক। প্রায় দু’ঘন্টার চেষ্টায় ঝাড়গ্রাম শহর থেকে লালগড় পৌঁছেছি। সাদা একটা বড় কাগজে ১০-১১ দফা দাবি লিখে রাস্তা থেকে উঠে দাঁড়াল সিদু সোরেন। তারপর তা পড়ে দেখলেন লালমোহন টুডু এবং আরও কয়েকজন। জমায়েতটা সব মিলিয়ে ৫০-৭০ জনের। এরপর সেই দাবি সনদ নিয়ে সিদু এবং আরও তিন-চারজন ঢুকে গেল লালগড় থানায়। দাবি সনদ থানায় জমা দিয়ে বেরিয়ে এল মিনিট পাঁচেকের মধ্যে। জানাল, মূল দাবি দুটো। জেলার পুলিশ সুপারকে গ্রামবাসীদের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে দলিলপুর চকে গিয়ে এবং লালগড় থানার ওসিকে উঠবোস করতে হবে কান ধরে। নয়তো লালগড়ে ঢুকতে দেওয়া হবে না পুলিশ-প্রশাসনকে। এরপরই আমার এবং অন্য সাংবাদিকদের ফোন নম্বর নিয়ে সিদু বলল, ‘দাদা কিছু ঘটলে জানাব।’ আমিও ওর নম্বর লিখে নিলাম। তারপর বহুবার ফোনে কথা হয়েছে সিদুর সঙ্গে। ওই বেশি ফোন করত। পুলিশ এবং সিপিআইএমের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ জানাতে। দু’তিন মাস পরেই আস্তে আস্তে বুঝতে পারছিলাম সিদুর ঘোরাফেরা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। ও আর একা যেখানে সেখানে যাচ্ছে না। সঙ্গে কিছু ছেলে থাকছে। হাঁটাচলায় সতর্কতা বেড়েছে। সঙ্গে যোগ হয়েছে সন্দেহপ্রবণ চাহনি। ১১ই নভেম্বর ২০০৮, লালগড় থানায় ঢুকে ডেপুটেশন জমা দেওয়া সিদু সোরেন কয়েক মাসের মধ্যেই হয়ে উঠল মোস্ট ওয়ান্টেড মাওবাদী নেতা। একটা আস্ত ১৫-২০ জনের দল তখন সিদুর নেতৃত্বে লালগড়, গোয়ালতোড়, সারেঙ্গার জঙ্গল দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। যে দাবি সনদ লালগড় থানায় জমা দিয়ে এল সিদু সোরেন এবং তার সহযোগীরা, তা মানার কোনও প্রশ্নই ওঠে না বলে সেদিনই বিকেলের মধ্যে স্পষ্ট করে দিল রাজ্য সরকারও। জেলার পুলিশ সুপার এবং থানার ওসি প্রকাশ্যে গিয়ে ক্ষমা চাইবেন এবং কান ধরে উঠবোস করবেন, এই অদ্ভুত দাবির পেছনে রয়েছে মাওবাদীরা, তাও জানাল সরকার। এদিকে লালগড় থানায় লালমোহ টুডু, সিদু সোরেনদের দাবিপত্র পেশের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তৈরি হল পুলিশ সন্ত্রাস বিরোধী জনসাধারণের কমিটি, যা কয়েক দিনের মধ্যেই পিসিপিএ নামে পরিচিত হয়ে গেল গোটা দেশে। নিজেদের দাবি সনদ নিয়ে তারাও নাছোড়। মুখমন্ত্রীর কনভয়ে বিস্ফোরণের পর পুলিশ লালগড়ের কাঁটাপাহাড়িতে গিয়ে মহিলাদের ওপর যে অত্যাচার করেছে তার জন্য ক্ষমা চাইতে হবে। কান ধরে উঠবোস করতে হবে। নয়তো লালগড়ে পুলিশ ঢুকতে দেওয়া হবে না। আর কোনও এলাকায় পুলিশকে ঢুকতে না দেওয়ার ‘নন্দীগ্রাম মডেল’ ততদিনে আমাদের জানা হয়ে গেছে। রাতারাতি লালগড় থানা থেকে কাঁটাপাহাড়ি যাওয়ার রাস্তায় বড় বড় খেজুর গাছ কেটে ফেলে দিল আন্দোলনকারীরা। লালগড়ের একটা বড় অংশকে প্রায় লিবারেটেড জোন তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেল সেদিনই। তারপর থেকে পরপর প্রায় দু’সপ্তাহ রোজ গেলাম লালগড়ে। দু’একদিনের মধ্যে রীতিমতো স্পষ্টও হয়ে গেল, ‘জনসাধারণের কমিটি’ নামেই। আসলে পুরোদস্তুর মাওবাদীরাই জনসাধারণকে সামনে রেখে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। অধিকাংশ মানুষই পুরনো সিপিআইএম বিরোধিতার জায়গা থেকে এই আন্দোলনের পাশে এসে দাঁড়ালেন। সিপিআইএম কিছু নেতা ঘরছাড়া হলেন। আর সিপিআইএমের সাধারণ কর্মী, সমর্থকরা ভয়ে-ভীতিতে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে হাঁটতে বাধ্য হলেন। ১২ কিংবা ১৩ই নভেম্বর হবে, সকাল সকাল অমিতাভর মোটরসাইকেলে চেপে আমি আর উজ্জ্বল ঝাড়গ্রাম থেকে লালগড়ের উদ্দেশে রওনা দিলাম। সেদিন কাঁটাপাহাড়িতে পিসিপিএ’র বড় মিটিং হওয়ার কথা। অন্যদিনের মতো হেঁটে কাঁসাই নদী পেরিয়ে রাস্তায় ফেলে রাখা খেজুর গাছ ঠেলতে ঠেলতে প্রায় দু’ঘন্টার চেষ্টায় তিনজনে গিয়ে পৌঁছালাম কাঁটাপাহাড়ি স্কুলের সামনে। সকাল সাড়ে দশটা মতো বাজে। গিয়ে দেখি আগেই দু’চারজন সাংবাদিক পৌঁছেছে। আমাদের পরেও এল বেশ কয়েকজন। সিদু সোরেন এবং পিসিপিএ’র নেতা গোছের কয়েকজনকে ঘিরে আমরা কথা বলছি। মিটিং শুরু হওয়ার কথা দুপুর বারটায়। আস্তে আস্তে কাঁটাপাহাড়ি স্কুলের সামনে ভিড় বাড়ছে। স্কুলের উল্টো দিকেই বড় মাঠ। মাঠ শেষ হলে শুরু হচ্ছে জঙ্গল। বারোটা-সাড়ে বারোটার পর থেকে দেখি, ওই মাঠে অল্প অল্প করে লোক আসতে শুরু করেছে আশপাশের গ্রাম থেকে। প্রতি দশজনে অন্তত ছ’জন মহিলা। আধ ঘন্টা-চল্লিশ মিনিটের মধ্যে মাঠে পাঁচ-সাতশ মানুষ জড়ো হয়ে গেলেন। কিন্তু আমরা, মানে কলকাতা এবং ঝাড়গ্রাম মিলে প্রায় ৩০-৩৫ জন সাংবাদিক তখনও বুঝতে পারছি না, মিটিংটা করবেন কে? সত্যিই শুধু সাধারণ গ্রামবাসীদের মিটিং নাকি মাওবাদী নেতৃত্বও যোগ দেবে তাতে? লোক তো জমায়েত হয়েছে খারাপ না। কিন্তু তখন আমাদের একটাই কৌতুহল, মিটিংয়ে বক্তৃতা কে করেন। সেটাই দেখার জন্য মাঠের পাশে আমরা সব জটলা করে দাঁড়িয়ে রয়েছি। রাস্তার পাশে লাইন দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখা আমাদের বাহন মোটরসাইকেল। কিছুক্ষণ বাদে আমাদের দিকে এগিয়ে এল সিদু। সঙ্গে দু’তিনজন। ‘আপনারা এবার এখান থেকে একটু চলে যান। এবার আমাদের মিটিং শুরু হবে।’ বেশ ভদ্রভাবেই আমাদের বলল সিদু সোরেন।‘কিন্তু আপনাদের মিটিং কভার করতেই তো আমরা এত দূর থেকে এসেছি।’‘না, মিটিংয়ের সময় আপনারা থাকতে পারবেন না। এক-দেড় কিলোমিটার দূরে গিয়ে অপেক্ষা করুন। মিটিং শেষ হলে আমরা জানিয়ে দেব কী সিদ্ধান্ত হল।’‘কিন্তু আমাদের তো মিটিংয়ের ছবি তুলতে হবে। এত লোক জমায়েত হয়েছে!’সিদুকে বোঝানোর চেষ্টা করল কয়েকজন সাংবাদিক। কিন্তু ততক্ষণে বেশ বুঝতে পারছি, যা দেখার এবং জানার জন্য এত রাস্তা কষ্ট করে মোটরসাইকেলে চেপে এসে এতক্ষণ অপেক্ষা করছি, তা ওরা আমাদের দেখতে দেবে না। আজকের মিটিংটা যে পুলিশ সন্ত্রাস বিরোধী জনসাধারণের কমিটির ডাকে নিছক গ্রামবাসীদের একটা সাধারণ জমায়েত নয়, তার একটা বারো আনা ধারণা ছিলই। কিন্তু সিদুর এই ভদ্রভাবে পেশ করা কঠিন স্বরে বাকি চার আনাও স্পষ্ট হল। তার মানে, মাওবাদীরা সত্যিই যোগ দেবে মিটিংয়ে! সিদু সোরেন স্রেফ নির্দেশ পালন করছে। অভিজ্ঞতায় দেখেছি, এই সব ক্ষেত্রে হাজার অনুরোধ করা মানে সময় এবং এনার্জি নষ্ট। লাভ কিছু হয় না। সাংবাদিকদের বহু অনুরোধেও সিদু সোরেন এবং তার সঙ্গীরা নিজের অবস্থান থেকে সরল না। শেষমেশ রফা হল, আমরা সবাই কাঁটাপাহাড়ির ওই মাঠের সামনে থেকে এক-দেড় কিলোমিটার দূরে সরে যাব। মিটিং শেষ হলে ওরা আমাদের ফোন করে ডেকে নেবে। তখন আমরা ছবি তুলে নেব। আর সঙ্গে জেনে নেব ওদের বক্তব্য। কাঁটাপাহাড়ি স্কুল থেকে পিচ রাস্তা একদিকে যাচ্ছে লালগড় থানার দিকে। অন্যদিকে যাচ্ছে রামগড়ের দিকে। আমি, হিন্দুস্থান টাইমসের সুরবেক বিশ্বাস এবং টেলিগ্রাফের প্রণব মন্ডল চলে গেলাম কয়েক কিলোমিটার দূরের রামগড়ে। থাকতেই যখন দেবে না, এক কিলোমিটার দূরও যা, কয়েক কিলোমিটার দূরের রামগড়ও তা। যাব-আসব তো মোটরসাইকেলে।রামগড়ে তাও কিছু দোকানপাট আছে। ঠিক আধা-শহর কিংবা গঞ্জ বলা যায় না। তবে রামগড়ে বাস স্ট্যান্ড আছে। দু’তিনটে ছোট ভাতের হোটেল আছে। পাকা বাড়ি আছে কিছু। ঠেলা গাড়িতে ফলের দোকান, গাড়ির টায়ার মেরামতির দোকান আছে। এসব কিছুই নেই কাঁটাপাহাড়িতে। এক বাক্যে বলা যায়, রামগড়ের বাসিন্দাদের কথায়-কথায় লালগড়ে যেতে হয় না। আমি, সুরবেক আর প্রণব রামগড়ে পৌঁছে গিয়ে বসলাম একজনের দোকানে। টায়ার মেরামতির দোকান। গল্প করলাম এক-দেড় ঘন্টা। কোন মাওবাদী নেতা আসতে পারে কাঁটাপাহাড়ির মিটিংয়ে তা নিয়ে কথা হল। যিনিই আসুন লালগড়ের মানুষকে আন্দোলনের রুপরেখা বোঝাতে, তিনি যে গুরুত্বপূর্ণ কেউ তা সিদুর কথাতেই স্পষ্ট। তা বুঝতেও পারছিলাম আমরা। কিন্তু এটাও ঠিক, লালগড় আন্দোলন যে কতটা ব্যাপকতা নেবে তা সেদিন রামগড়-কাঁটাপাহাড়িতে বসে আমরা কেউই আন্দাজ করতে পারিনি। সেদিন আমাদের কারও মাথাতেও আসেনি সিপিআই (মাওয়িস্টের) পলিটব্যুরো সদস্য কোটেশ্বর রাও ওরফে কিষেণজি এই আন্দোলনকে নেতৃত্ব দেবেন। আড়াইটে-তিনটে নাগাদ আবার ফিরলাম কাঁটাপাহাড়ি। মিটিংয়ের মাঠের পাঁচ-সাতশ মিটার দূরে থামলাম। অন্যান্য সাংবাদিকরাও সেখানে অপেক্ষা করছে। আরও ঘন্টাখানেক বাদে আমাদের সব ডাক পড়ল কাঁটাপাহাড়ির মাঠে। প্রায় চারটে বাজে। কাঁটাপাহাড়ির মাঠে পৌঁছে দেখি সাত-আটশো পুরুশ-মহিলা তখনও মাটিতে বসে। স্কুলে যেমন লম্বা টেবিল আর বেঞ্চ থাকে তেমন পাতা রয়েছে। সেই বেঞ্চে বসে আছে নেতা স্থানীয় তিন-চারজন। সেই বেঞ্চে বসেই শুরু হল লালমোহন টুডু এবং সিদু সোরেনের সাংবাদিক বৈঠক। দু’জনে একই কথা বললেন, ‘গ্রামবাসীরা আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তল্লাশির নামে পুলিশ মহিলাদের ওপর যে অত্যাচার করেছে তার জন্য ক্ষমা না চাইলে পুলিশকে লালগড়ে ঢুকতে দেওয়া হবে না। ওসিকে কান ধরে উঠবোস করতে হবে। এসপিকে ক্ষমা চাইতে হবে। নয়তো রাস্তা বন্ধ করে রাখা হবে। আন্দোলন চলবে।’বিকেল প্রায় পাঁচটা নাগাদ কাঁটাপাহাড়ি ছাড়লাম। ঝাড়গ্রামে পৌঁছতে ঘণ্টা দেড়েক লেগে যাবে প্রায়। তারপর সারাদিন যা যা ঘটেছ তার ছবি, খবর পাঠাতে হবে অফিসে। রাস্তায় ফেলা খেজুর গাছ পেরিয়ে যতটা সম্ভব জোরে মোটরসাইকেল চালাচ্ছে অমিতাভ। ঠান্ডা একটা হাওয়া দিচ্ছে, সন্ধে নামছে জঙ্গলমহলে। বুঝতে পারছিলাম, লালগড়ের এই আন্দোলন সহজে থামার নয়। পুলিশ সন্ত্রাস বিরোধী জনসাধারণের কমিটি নামেই। মাওবাদীরা আন্দোলনটা টেকওভার করে নিয়েছে। নাকি টেকওভার নয়, ২রা নভেম্বর থেকে এটা ওদেরই আন্দোলন? আজকে মিটিংয়ের আগে যামাদের যে সেখান থেকে বের করে দেওয়া হল, তার পরে মাওবাদীদের অ্যাক্টিভ ইনভলভমেন্ট নিয়ে আমার আর কোনও সংশয় নেই। তারও বেশ কয়েক দিন বাদে নিশ্চিত হয়েছিলাম, মাওবাদীরা টেকওভার করে নেয়নি মোটেও, আন্দোলনটা ওদেরই ছিল। পিসিপিএ ছিল একটা মুখোশ মাত্র। আন্দোলন সম্পর্কে কলকাতা সহ দেশের মানুষ এবং সিভিল সোসাইটিকে একটা ভিন্ন বার্তা দিতেই তৈরি করা হয়েছিল পিসিপিএ। যাতে মনে হয় পুলিশের অত্যাচারের বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফুর্তভাবে ফুঁসে উঠেছে সাধারণ মানুষ। যা কিছুদিনের মধ্যেই বিভিন্ন মানুষের যথেষ্ট সহানুভুতিও পেয়েছিল। পরে বারবার বিভিন্ন অভিজ্ঞতায় স্পষ্ট হয়েছে, ২রা নভেম্বর বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এবং রামবিলাস পাসোয়ানের কনভয়ে অ্যাটাক মাওবাদীরা করেছিল একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়েই। এই অ্যাটাকের পর গ্রামে পুলিশের অভিযান হবে এবং তাকে কেন্দ্র করে পিসিপিএর মতো কোনও কমিটি তৈরি করে আন্দোলনের উর্বর জমির প্রস্তুতিও করে রেখেছিল তারা। অথচ, ইতিহাসের কী নির্মম পরিণতি, যে পিসিপিএ গড়ে উঠেছিল মাওবাদীদের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে, যা দিনের পর দিন মাওবাদীদের বর্মের কাজ করেছে, পুলিশের হাত থেকে রক্ষা করেছে শীর্ষ নেতাদের, সেই কমিটিই কিনা এক সময় মৃত্যুবাণ হাতে তুলে নিল তাদের বধ করতে! ২০১১ সালের শেষে কিষেণজির তো বটেই, ২০১০ সালের মাঝামাঝি থেকেই যে বিভিন্ন এনকাউন্টারে একের পর এক সাফল্য পেতে শুরু করেছিল পুলিশ এবং সিআরপিএফ, তার প্রায় প্রতিটাতেই ছিল পিসিপিএর কোনও না কোনও নেতার গোপন ভূমিকা। মাওয়িস্ট নেতারা জানতেও পারেননি, তাঁদেরই হাতে গড়ে তোলা পিসিপিএর কোন কোন সদস্য তাঁদের সম্পর্কে ইনফর্মেশন দিচ্ছে পুলিশকে।ক্রমশ...।
জনতার খেরোর খাতা...
যাকে তোমরা ঈশ্বর বলো - পাগলা গণেশ | প্রতিবারে কেন ঈশ্বর জিতে যায়?প্রিয়জনের প্রাণ কেড়ে নিলেও ভালো করে,প্রাণ দিলেও ভালো।কি করে হতে পারে?দেশের পর দেশ উজাড় করেও কি করে ভালো হতে পারে?কি করে গরিবকে দিনের পর দিন অভুক্ত রেখেও ভালো হতে পারে?তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে নাকি পাতাও নড়তে পারে না,তোমার সমস্ত পুণ্যের দায় তার,কিন্তু যেই পাপ করলে,তখন সে ঘাড় সরিয়ে নেবে সুড়ুৎ করে,সেটা নাকি তোমার দোষ!কেউ দেখেনি তাকে,কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই,তবু সবাই গভীর বিশ্বাস করে,কেউ ভয়ে, কেউ লোভে, কেউ স্বার্থে।তার জন্য খুন করতে পারে লোকে,খুন হতে পারে।এত ভুলে ভরা চরিত্র, এত চরিত্রহীন, দুশ্চরিত্র;মানুষ হলে কয়েক লক্ষ বার ফাঁসি হত।কিন্তু তার হয় না।প্রচন্ড স্বেচছাচারী, আত্মমগ্ন, স্তুতিপ্রেমী,কিন্তু তবু নাকি মহান!সব ধর্মগ্রন্থ পড়ে একটিই নির্যাস পাওয়া যায়,মানুষকে সে সৃষ্টি করেছে বন্দনার তরে।কী আত্মপ্রেমী, কল্পনা করা যায়!এমন জিনিস মহান হতে পারে না,না হয় থাকতে পারে না।দ্বিতীয়টাই সম্ভব।মানুষ নিজের দরকারে বানিয়েছে তারে,অমন কেউ না।সভ্যতার আগে, মানুষের ভয়ের সময়ে,অসহায় মানুষ বানিয়েছিল তাকে,নিজেকে প্রবোধ দেওয়ার জন্য,তাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করে গেছে অহর্নিশ,পুতুলখেলা করে গেছে,নিজেদের বানানো নিয়ম অনুসারে।হেদুয়ার ধারে - ১৪৩ - Anjan Banerjee | নিখিল ব্যানার্জী বললেন, ' কাবেরী বোস ... কিন্তু ... 'সাগর বলল, ' ঠিক বোঝাতে পারব না স্যার। কিন্তু আমার মনে হয় ও পারবে ... জান দিয়ে চেষ্টা করবে ... সেটা ঠিক কি কারণে বলতে পারছি না ... '----- ' হুমম্ ... দেখা যাক, বলছ যখন ... তোমার অনুমান তো ভুল হবার নয় ... কিন্তু ও রাজি হবার ব্যাপার তো আছে। '----- ' হ্যাঁ ... সে তো বটেই। ওটা আপনার ওপর নির্ভর করছে ... 'নিখিলবাবু বললেন, ' হুমম্ ... দেখি কি হয়। এমনিতেই তো মেয়েটি বেশ বাধ্য বলেই মনে হয় ...'----- ' হ্যাঁ ... তা ঠিক। আপনার খুবই বাধ্য। হয়ত আপনার কিছু বলার বলার দরকার হল না ... তার আগেই প্রমাণ পেয়ে গেলেন ... '------ ' কিসের প্রমাণ ? '----- ' এই ... আপনাকে যে মেনে নিয়েছে তার প্রমাণ। ওই... আনুগত্য না কি বলে ... '----- ' ও আচ্ছা আচ্ছা ... ঠিক আছে কথা বলব। ওর কথা এখন রাখ। অনেক কাজের কথা আছে ... '----- ' হ্যাঁ স্যার বলুন ... 'নিখিলবাবু সাগরের সঙ্গে সংগঠন সম্পর্কিত কিছু গূঢ় কথা আলোচনা করতে লাগলেন। সাগর খুব মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগল।বিভূতিবাবুর সত্তর বছর বয়স হয়ে গেল। তিনি আজকাল খালি ভাবেন পৃথিবীটা অনেক পুরণো হয়ে গেল তার চোখের সামনে। তবে আরও অনেক পুরণো লোকের মতো তিনি বলতে চান না, এবার গেলেই হয় ...। তার মনে হয়, আরও অনেক দিন ধরে আরও অনেক কিছু দেখবেন এই হেদুয়ার ধারে। আরও কত লোক যাবে আসবে রামদুলাল সরকার স্ট্রিট, বেথুন রো, ডাফ স্ট্রিট, বিডন স্ট্রিটের অলিগলি, ঘর বাড়িতে। নানা কেতার, নানা মোড়কের নারী পুরুষ ঘুরবে ফিরবে, কথাবার্তা কইবে। নতুন অন্য নাটক, অন্য চরিত্র, অন্য ডায়লগ, শুধু মঞ্চটা একই ... হেদুয়ার ধারে।বিভূতিবাবু ঘরকুণো মানুষ। তিনি এই গঙ্গাপদ, জন্মেজয়বাবু, নিতাইবাবু আর হাতিবাগানের সিনেমা থিয়েটার পাড়া নিয়ে বেশ আছেন। সারা দুনিয়া ঘুরে দেখার কোন বাসনা বা কৌতূহল তার নেই। দীনবন্ধুকে নিয়ে মিনার্ভায় অঙ্গার দেখতে যাওয়ার কথা মনে পড়ল। বিভূতিবাবু ভাবলেন, দীনবন্ধু কিন্তু বেশ ভাল পার্টনার ছিল তার। ওকে নিয়ে স্টার, মিনার্ভা রঙমহলে বেশ কয়েকটা থিয়েটার দেখেছেন তিনি। দীনবন্ধু সংসার পাততে চলেছে। সে কি আর আগের মতো সময় দিতে পারবে। তার নাতির নাম রাখা হয়েছে ঋতবান। সে দিনে দিনে শশীকলার মতো বেড়ে উঠছে। এই জীবনের বাগানে এক নতুন মায়াবৃক্ষ পল্লবিত হয়ে উঠছে তার লতায় পাতায় জড়িয়ে ধরার জন্য।রাস্তায় সেদিন সুরেশ্বর মল্লিকের সঙ্গে দেখা হল।লোকটা ধীরে ধীরে কেমন বদলে গেল। বদ অভ্যাস সব ছেড়ে দিয়েছে। সে রাস্তার ওপারে খারাপ পাড়ায় যাওয়াই হোক কিংবা ইয়ার বক্সী মিলে ঢালাও নেশার মোচ্ছব করাই হোক। সাগরই বোধহয় বদলে দিল তাকে।সুরেশ্বর বলল, ' আরে বিভুতদা, কি খবর ... কেমন আছেন ? '----- ' এই আছি একরকম ... তুমি কেমন আছ ? '----- ' আগের চেয়ে ভাল। হুজ্জুতির মধ্যে জীবন কাটানোটা খুব খারাপ... বুঝলেন তো ? '----- ' হুজ্জুতির মধ্যে জীবন কাটানো মানে ? '----- ' মানে ... এই, হুঁশোর মতো এটা ওটা চাখতে ছোটা আর কি .... আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ লোক, আপনাকে আর কি বোঝাব ... '------ ' অ ... তা বটে। সাগরের সঙ্গে দেখা হয়েছিল নাকি ? '----- ' হ্যাঁ, কালকেই দেখা হয়েছিল রাজকৃষ্ণ স্ট্রিটে। বাড়িভাড়া আদায় করতে গিয়েছিলাম। অনেকক্ষণ কথা বলল। সাগর আমার সঙ্গে এত কথা আগে কোনদিন বলেনি। বলছিল ওদের কি একটা সংগঠন হয়েছে। লোকের ভালমন্দ দেখা নাকি ওদের কাজ। তা সাগর তো চিরকালই তাই করছে। এ আর কি নতুন কি। তবে একটা দল তৈরি করে করলে অনেকটা সুবিধে হতে পারে .... ভাল ভাল .... সাগরের ওপর আমার বিশ্বাস আছে ... '------ ' হ্যাঁ, তা ঠিক। আমারও খুব ভরসা ওর ওপর ... বুঝলে ... ' বিভূতিবাবু সমর্থন জানালেন।----- ' আর বলছিল যে, ওদের দলের নাকি একজন মাথা আছে। তিনি নাকি একজন অঙ্কের প্রফেসর ... বোঝ কান্ড ! সাগর বলল, আমার যদি আগ্রহ থাকে তাহলে নাকি ও স্যারের সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবে। বোঝ কান্ড ... আমার মতো একটা লোক ... কি যে বলে ... হ্যা হ্যা ... সে যাই হোক, যেহেতু সাগর বলছে আমি ওদের সংগঠনে যোগ দিতে রাজি হয়েছি। আমাকে একদিন নিয়ে যাবে স্যারের কাছে। দেখি কবে বলে ... '----- ' অ ... তাই নাকি ? আমি তো এসব এই প্রথম শুনলাম। আচ্ছা ... গিয়ে বোঝ তো ব্যাপারটা কি ... একটু বোল তো আমাকে .... '----- ' হ্যাঁ, নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই ... আপনার নাতি ভাল আছে তো ? '----- ' হ্যাঁ তা ... সকলের আশীর্বাদে আছে মোটামুটি ... ভাল বলতে ভয় লাগে ... কি বলব ... '----- ' না না কোন চিন্তা করবেন না। ভাল হবে, খুব ভাল হবে ... 'বিভূতিবাবু উদাসভাবে বললেন, ' তাই যেন হয় ...তুমি তা'লে ওখান থেকে ঘুরে এসে ব্যাপারটা জানিও ... '----- ' কোথা থেকে ঘুরে এসে বলুন তো ? '---- ' ওই যে বললে সাগর তোমায় কোন স্যারের কাছে নিয়ে যাবে ... '------ ' ও আচ্ছা... নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই ... বললাম তো ... 'সুরেশ্বরকে নিয়ে একদিন নিখিল ব্যানার্জীর বাড়িতে হাজির হল সাগর।নিখিলবাবুকে দেখে সুরেশ্বর বলল, ' নমস্কার স্যার ... 'নিখিলবাবু মল্লিকবাবুর দিকে এগিয়ে গিয়ে বললেন, ' আমায় নমস্কার করবেন না দাদা .... আসুন আমরা আলিঙ্গন করি ... ', বলে সুরেশ্বরকে আন্তরিকভাবে আলিঙ্গন করলেন।তারপর বললেন, ' বসুন বসুন ... 'সুরেশ্বর বেশ অভিভূত হয়ে গেল বলা যায়। এর আগে আজ পর্যন্ত কেউ তাকে সম্মানসূচকভাবে আলিঙ্গন করেনি। ভালবেসে তো নয়ই।সে কি বলবে ঠিক ভেবে পেল না। পচা দাগধরা লোকজন নিয়ে তার জীবন কেটেছে সেই ছোটবেলা থেকে। পারিবারিক ধনের গর্ব এবং নানা অনুচিত প্রবণতায় জড়িয়ে কেটেছে বাল্যকাল থেকে। কিন্তু একটা পুণ্যভূমি বোধহয় পড়ে ছিল তার মনের পৃথিবীর এক কোণায়। সাগর হয়ত নিজের অজান্তেই সেই জমিটার জঙ্গল আগাছা সাফ করে তাকে কর্ষনযোগ্য করে তুলেছে।----- ' আমি স্যার ওই রামদুলাল সরকার স্ট্রিটে থাকি ... মল্লিকবাড়ি। ওখানেই জন্ম। আমার বাপ ঠাকুর্দারও ... মানে ওখানেই। সাগরবাবু আমায় ভাল চেনে ... খানদানের পয়সা ছিল ... শিক্ষা ছিল না ... তেমন সুযোগ পাইনি স্যার ... অনেক উল্টোপাল্টা ইয়ে করে ফেলেছি জীবনে ফালতু লোকের সঙ্গে মিশে ... কি বলব ... 'নিখিলবাবু মনোযোগ দিয়ে সুরেশ্বরের কথা শুনছিলেন।তিনি বললেন, ' আরে দাদা আমার ... আপনি শিক্ষিত নয় এ কথা আপনাকে কে বলল। শিক্ষা মনের ভিতরে থাকে। সেটা যে বার করে আনতে পারে সেই তো মানুষ। আপনি তো তা পেরেছেন। তাছাড়া এ পৃথিবীর প্রাণীকূলের মধ্যে একমাত্র মনুষ্য প্রজাতিই নিজের ভুল বুঝতে পারে এবং আপনি তা পেরেছেন। বেশির ভাগই মনুষ্যরূপীঅমানুষ সেটা নিশ্চয়ই আপনি অনেকের চেয়ে ভাল জানেন। আপনি জীবনের খারাপ দিকগুলো দেখে নিয়েছেন। সুতরাং ভাল দিক চিনে নিতে আপনার অসুবিধে হবার কথা নয়। 'এই সময়ে সুরেশ্বর মল্লিক জোর গলায় বলে উঠল, ' একদম একদম ... 'নিখিলবাবু এক গাল হেসে বললেন, ' তবে ? 'সুরেশ্বরবাবু ঘোরপ্যাঁচ বিশেষ বোঝেন না। তিনি এবার সরাসরি জিজ্ঞাসা করলেন, ' আমাকে কি করতে হবে ? 'নিখিলবাবু আচমকা এরকম একটা প্রশ্ন শুনে একটু থমকে গেলেন।একটু চুপ করে থেকে তারপর বললেন, ' অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন মল্লিকদা .... আপনার উপযুক্ত কাজই আপনি পাবেন ... 'এই সময়ে সাগর হঠাৎ জানলার দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, ' কে এ এ এ ? কে রে এ ?জানলা থেকে মুখটা সরে গেল পলকে।সাগর বুলেটের মতো ছিটকে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। ( চলবে )********************************************যেমন কাটছে দিন - SAUMITRA BAISHYA | লালমোহনবাবুর একেবারে সম্প্রতিক খবর যারা জানেন না, তাঁদের জানিয়ে রাখি, লালমোহনবাবু তাঁর সাধের এম্বেসেডার গাড়িটি প্রাণে ধরে বিক্রি করতে পারেননি বটে, তবে একটা হন্ডা সিটি আর একটা এসইউভি গাড়ি কিনেছেন। হন্ডা সিটি গাড়িটাই সবসময় চড়েন। এসইউভি গাড়ি সম্পর্কে তাঁর অভিমত হল, ওটা চড়লে বয়সটা কমে গেছে বলে মনে হয়। তখন তিনি চক্রাবক্রা শার্ট আর প্যান্ট পরেন। আর দূরে কোথাও বেড়াতে গেলে, এসইউভি গাড়িটা তাঁর পছন্দ। ফেলুদা অবিশ্যি বলে, যে আগেকার রাজাদের ঘোড়াশালে যেমন ঘোড়া থাকত, লালমোহন বাবুর অবস্থাও হয়েছে তেমন। শুনে লালমোহন বাবু হেসে দু'কানে হাত দিয়ে বলেন, আর লজ্জা দেবেন না মশাই। তবে ইদানিং যেসব রহস্য উপন্যাস প্রকাশিত হয়, সেই বাজারে প্রখর রুদ্র আর কাটে না। তাছাড়া, একালের প্রজন্ম ভূত প্রেত, তান্ত্রিক কাহিনী বেশী পছন্দ করে। তোপসে বুদ্ধি দিল, ওটিটি চ্যানেলের জন্য রহস্য কাহিনী লিখুন। লালমোহনবাবুর কাহিনী নিয়ে কিছু সিনেমাও হয়েছিল। তাই, ওটিটি চ্যানেলের দরজা পেরোতে অসুবিধা হল না। হুলুস্থূল চ্যানেলের সাথে লালমোহনবাবুর চুক্তি হয়ে গেল। প্রথম সিরিজেই কিস্তিমাত। ওদিকে মগনলাল পুরোনো বেওসা ছেড়ে প্রমোটারের ব্যবসার সাথে শেয়ার বাজারেও টাকা খাটায়। ঘটনাচক্রে মগনলালের সাথে লালমোহনবাবুর দেখা হয়ে যায় এক ফিল্ম স্টুডিওর চত্বরে। লালমোহনবাবু চিনতে না পারলেও, মগনলাল ঠিক চিনে ফেলে লালমোহনবাবুকে। কী লালুবাবু, কেমন আছেন? এই কণ্ঠস্বর লালমোহনবাবু জীবনেও ভুলতে পারবেন না। চাকু ছুঁড়ে মারার দৃশ্যটা মনে পড়ে গেল। এদিকে মগনলাল তো নাছোড়বান্দা। সে লালমোহনবাবুকে চা না খাইয়ে ছাড়বে না। চা খাওয়াটা অজুহাত। আসলে, লালমোহনবাবুর যে এখন অনেক টাকা হয়েছে, সেটা মগনলাল জানত। সে বলল, লালুবাবু, টাকা ব্যাংকে ফেলে না রেখে, রিয়েল এস্টেটে লাগান। অনেক বেশী রিটার্ন পাবেন। একটা ভিজিটিং কার্ড দিয়ে বলল, এটা রাখুন। আপনার ফেলুবাবুর সাথে আলাপ করিয়ে লিবেন। আর উনাকে বলে দেবেন, আমি এখন সাদা বেওসা করি। তোপসেকে দিয়ে মগনলালকে ফোন করিয়ে নিল। আরো কিছু খবর নিয়ে ফেলুদা নিশ্চিত হল যে আগের মগনলাল বদলে গেছে। ফেলুদার পরামর্শ পেয়ে লালমোহনবাবু কিছু টাকা এম.এল. কনস্ট্রাকশনে লাগালেন। লালমোহনবাবু প্রথম দফায় বেশ ভালো লাভ পেলেন।সেদিন একেবারে সাত সকালেই লালমোহনবাবু গড়পার থেকে এসে হাজির। দুই চোখ লাল। ফেলুদা সদ্য কিছু ফ্রি হ্যান্ড আর যোগাসন করে, চারমিনার ধরিয়ে হিন্দু পত্রিকাটা তুলে নিয়েছে। লালমোহনবাবু রাত জেগে টিভিতে এক্সিট পোল দেখেছেন। চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, একটা প্রশ্ন ছিল। ফেলুদা পত্রিকা থেকে চোখ না তুলে বলল, সে তো আপনার সাত সকালে আসাতেই বুঝতে পারছি। তবে রাজনীতি নিয়ে কোনো প্রশ্ন নয়।লালমোহনবাবু এক গাল হেসে বলে ফেললেন, আপনি তো আর প্রধানমন্ত্রী নন।ফেলুদা এবার পত্রিকা নামিয়ে রেখে বলল, ছেলে ছোকরারা আপনাকে আর আমাকে নিয়ে কী সব মিম বানিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছেড়েছে, সেসব দেখেছেন ? এমনকি তোপসেকেও ছাড়েনি।লালমোহনবাবু সহজে দমবার পাত্র নন। বললেন, আরে, এসব তো জনপ্রিয়তা বাড়ায়। কী ভাই তোপসে, তুমি তো এসব বোঝ।তোপসে কিছু বলার আগেই, ফেলুদা বলল -- ও কী বলবে। যা হয়েছে একদম ভালো হয়নি। ব্রডকাস্টিং বিলটা আইন হয়ে গেলে, জেলেও যেতে হতে পারে।লালমোহনবাবু বললেন, তাহলে একটা এন্টিসিপেটরি বেইল নিয়ে রাখলেই হয়।ফেলুদা এভাবে কখনো হাসে না। হাসতে হাসতে বলে, কিসের ভিত্তিতে জামিম চাইবেন? আপনি কি বায়োলজিক্যাল?হতভম্ব লালমোহনবাবু বললেন -- তবে কি আমরা বোটানিক্যাল?#যেমন_কাটছে_দিন
ভাট...
 lcm | হ্যাঁ, এটা গ্লোবাল ফাইন্যান্স মার্কেটে উল্লেখযোগ্য খবর। পঞ্চাশ বছর আগে ১৯৭৪ সালে সৌদি সরকারের সঙ্গে একটা চুক্তি হয়েছিল যে পৃথিবীর যে কোনো দেশ যখন সৌদি থেকে তেল (ক্রুড অয়েল) কিনবে, কেবল মাত্র ইউএস ডলারে পেমেন্ট গ্রাহ্য হবে। সেই চুক্তি ৫০ বছরের জন্য ছিল। সেটা শেষ হয়ে গেল ২০২৪-এ, এটা আর রিনিউ করে নি সৌদি সরকার। তো এতে করে এতদিন যেটা হত, সেটা হল বিভিন্ন দেশ তাদের বৈদেশিক মুদ্রা ইউএস ডলারে সঞ্চয় করত, তেল কিনতে কাজে লাগবে, এইসব কারণে। এখন থেকে ইউএস ডলারে আর ট্রেড হবে না তা নয়, তবে অন্য কারেন্সিতেও হবে। এই যেমন, সৌদি বলছে চাইনিজ ইউয়ান পেমেন্ট নেবে। অলরেডি চায়নার সঙ্গে ৫০ বিলিয়ন ইউয়ান এর একটা ডিল করে ফেলেছে। তাছাড়া, বিটকয়েন পেমেন্ট ও নেবে ভাবছে।
lcm | হ্যাঁ, এটা গ্লোবাল ফাইন্যান্স মার্কেটে উল্লেখযোগ্য খবর। পঞ্চাশ বছর আগে ১৯৭৪ সালে সৌদি সরকারের সঙ্গে একটা চুক্তি হয়েছিল যে পৃথিবীর যে কোনো দেশ যখন সৌদি থেকে তেল (ক্রুড অয়েল) কিনবে, কেবল মাত্র ইউএস ডলারে পেমেন্ট গ্রাহ্য হবে। সেই চুক্তি ৫০ বছরের জন্য ছিল। সেটা শেষ হয়ে গেল ২০২৪-এ, এটা আর রিনিউ করে নি সৌদি সরকার। তো এতে করে এতদিন যেটা হত, সেটা হল বিভিন্ন দেশ তাদের বৈদেশিক মুদ্রা ইউএস ডলারে সঞ্চয় করত, তেল কিনতে কাজে লাগবে, এইসব কারণে। এখন থেকে ইউএস ডলারে আর ট্রেড হবে না তা নয়, তবে অন্য কারেন্সিতেও হবে। এই যেমন, সৌদি বলছে চাইনিজ ইউয়ান পেমেন্ট নেবে। অলরেডি চায়নার সঙ্গে ৫০ বিলিয়ন ইউয়ান এর একটা ডিল করে ফেলেছে। তাছাড়া, বিটকয়েন পেমেন্ট ও নেবে ভাবছে। dc | ওদিকে সৌদি আরাবিয়া পেট্রোডলার চুক্তি আর রিনিউ করলো না। এর ফলে ডলার হয়তো খানিকটা পড়বে আর আমেরিকার ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেটও খানিকটা দুর্বল হয়ে যাবে। এদ্দিন ডলার আস্তে আস্তে তিরাশি টাকায় উঠেছিল, সুন্দর দাম উঠছিল, এখন কি হবে কে জানে। হায় হায়! :-(
dc | ওদিকে সৌদি আরাবিয়া পেট্রোডলার চুক্তি আর রিনিউ করলো না। এর ফলে ডলার হয়তো খানিকটা পড়বে আর আমেরিকার ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেটও খানিকটা দুর্বল হয়ে যাবে। এদ্দিন ডলার আস্তে আস্তে তিরাশি টাকায় উঠেছিল, সুন্দর দাম উঠছিল, এখন কি হবে কে জানে। হায় হায়! :-( যোষিতা | Pride parades in: Zurich (15 June) London (29 June) Milan (29 June) Madrid (06 July) Berlin (27 July) Amsterdam (03 August) Stockholm (03 August)
যোষিতা | Pride parades in: Zurich (15 June) London (29 June) Milan (29 June) Madrid (06 July) Berlin (27 July) Amsterdam (03 August) Stockholm (03 August)
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজামহারাজ ছনেন্দ্রনাথ ও বিদেশি চকলেটের বাক্স - রমিত চট্টোপাধ্যায়
১৫ জুন ২০২৪ | ৩০ বার পঠিতআজকে সকালে তেতলার পিসিমার কাছে যে চিঠিটা এল, দাদা মানে পিসিমার ছেলে অনেকক্ষণ ধরে পিসিমাকে পড়ে পড়ে শোনাচ্ছে। ছেনু গিয়ে দু'বার দরজার সামনে থেকে ঘুরেও এল, কত লম্বা চিঠি রে বাবা! শেষে আর থাকতে না পেরে ছেনু গিয়ে পিসিমাকে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করেই ফেলল, কার চিঠি গো? দেখা গেল অদ্ভুত ব্যাপার, পিসিমা হাসছে, অথচ চোখের কোণে জল, পিসিমা হেসে বলল, কে আসছে জানিস? কান্টু আসছে রে কান্টু, তোর কান্টু দাদা। এদ্দিন পর ও আসছে, শুনে বিশ্বাসই করতে পারছি না, তাই তো বারবার করে শুনছি। ছেনু ছোট্ট থেকে পিসিমার কাছে কান্টুদার অনেক গল্প শুনেছে, কিন্তু কোনোদিন কান্টুদাকে চোখে দেখেনি আজ পর্যন্ত। অবশ্য দেখবেই বা কি করে, ছেনুর জন্মের আগেই তো পিসিমার বড় ছেলে কান্টুদা সেই সাত সমুদ্দুর তেরো নদী পার করে কি একটা দেশ আছে, কানাডা না কি নাম, সেইখানে চলে গিয়েছিল। সেই থেকে সেখানেই থাকে আর মাঝে মধ্যে চিঠি লিখে খবরাখবর জানায়। শুরুর দিকে বাংলায় লিখত বটে কিন্তু পরে কি জানি কেন শুধু ইংরেজিতেই চিঠি পাঠায়, তাই অন্যরা পিসিমাকে তর্জমা করে পড়ে পড়ে শোনায় কি লিখেছে।
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাবিপ্লবের আগুন - পর্ব নয় - কিশোর ঘোষাল
১৫ জুন ২০২৪ | ১৮ বার পঠিততোমার মনে আছে, কবিরাজদাদা ওর শরীরের লক্ষণ দেখে বলেছিলেন, ভল্লা সাধারণ এলেবেলে ছেলে নয়। যথেষ্ট শক্তিশালী যোদ্ধা। আরও বলেছিলেন, ওই চরম অসুস্থ অবস্থায় ওর এখানে আসাটা হয়তো আকস্মিক নয়। হয়তো গোপন কোন উদ্দেশ্য আছে। আজকে সকলের সামনে কবিরাজদাদা সে প্রসঙ্গ তোলেননি। কিন্তু আমারও এখন মনে হচ্ছে কবিরাজদাদার কথাই ঠিক”।
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাফৈজান আহমেদ আত্মহত্যা করেন নি - অমিতাভ চক্রবর্ত্তী
১৫ জুন ২০২৪ | ২৯১ বার পঠিতনির্মম হত্যাকান্ড! খুন হয়েছিলেন আই আই টি খড়গপুরের মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র ফৈজান আহমেদ? কি ভাবে? গত ২১শে মে ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ ডক্টর অজয় গুপ্তা কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর বেঞ্চকে জানান যে ফৈজানকে মাথার পিছনে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হয়েছিল, ঘাড়ের জায়গায় ছুরির আঘাত করা হয়েছিল এবং তার পর পিছন থেকে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে ঘাড়ে গুলি করা হয়েছিল। (১৩-ই জুনের ই-নিউজরুম ইন্ডিয়ার প্রকাশিত সংবাদ)। এই রিপোর্ট মৃতদেহের দ্বিতীর ময়নাতদন্তের ফল। কেন দু’বার ময়নাতদন্ত? কারণ, প্রথম ময়নাতদন্তে এতগুলি চিহ্নর কোন কিছু নজরে আসে নি আর মৃত্যুর কারণ সাব্যস্ত হয়েছিল আত্মহত্যা। নিজের হস্টেল ঘর থেকে ২৩ বছরের ছেলেটির অর্ধ-গলিত মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল। আই আই টি কর্তৃপক্ষ এবং পুলিশের বক্তব্য অনুসারে তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন। ফৈজানের মৃত্যুর খবর পেয়ে তার পরিবার খড়গপুরে পৌঁছে তার মৃতদেহ দেখে এই মৃত্যুকে আত্মহত্যা বলে মানতে অস্বীকার করেন। তারা বলেন ফৈজান র্যাগিংয়ের শিকার এবং তিনি খুন হয়েছেন। ফৈজানের মা-বাবা কলকাতা হাইকোর্টে পিটিশন দাখিল করেন। পোস্ট-মর্টেম রিপোর্টে অসঙ্গতি নজরে আসায় হাইকোর্ট মৃতদেহ কবর থেকে তুলে নিয়ে এসে দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্ত করার আদেশ দেয়।
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাজাগছে সেঙ্গল! অরণ্য আর আদিবাসী উৎপাটনের হুংকার - নরেশ জানা
১৫ জুন ২০২৪ | ৫৪ বার পঠিত২০১৮-র ডিসেম্বরে পার্লামেন্টে সরকার জানায় যে, ২০১৫ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে মোট ২০,৩১৪.১২ হেক্টর বনভূমি কর্পোরেট সংস্থার হাতে খনিজ পদার্থ উত্তোলনের জন্য তুলে দেওয়া হয়েছে। যদিও আদিবাসীদের আন্দোলন, গ্রামসভা গুলির আপত্তি ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে কর্পোরেট সংস্থাগুলোর পক্ষে কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ায় কিছু সমস্যা হচ্ছিল, বিশেষ ছত্তিশগড়ের গভীর অরণ্য বেষ্টিত আদিবাসী জনজাতি নির্ভর এলাকাগুলিতে। ২০২৩ সালের নভেম্বরে ছত্তিশগড়ে বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসকে পরাজিত করে সরকার গঠন করে বিজেপি। এখানেও কায়দা করে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী করা হয় বিজেপির আদিবাসী নেতা বিষ্ণু দেও সাই কে। ২০২৪ ডিসেম্বর মাসে শপথ নেন তিনি আর জানুয়ারি থেকেই গৌতম আদানির কোম্পানি শুরু করেছে নির্বিচার অরণ্য নিধন।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালবৈঠকি আড্ডায় ১৮ - হীরেন সিংহরায়
১৫ জুন ২০২৪ | ৫৪ বার পঠিতগাড়ির ড্যাশ বোর্ডের স্পিডোমিটার দেখলে জানা যায় তাঁর উচ্চতম গতি বেগ ঘণ্টায় দুশো কিলোমিটার । এই সব মূল্যবান তথ্য জানিয়ে বিক্রেতারা মহার্ঘ্য গাড়ি বিক্রি করেন । গাড়ির শো রুম থেকে বেরুলেই চোখে পড়ে নোটিস - শহরের ভেতরে গাড়ির গতির উচ্চসীমা ঘণ্টায় বিশ মাইল, একটু দূরে গেলে তিরিশ। মোটরওয়েতে ৭০ মাইল ( ১১২ কিমি ) গতি অনুমোদিত । সেখানে কদিন যাই ? যেখানে আমার নিত্যিদিনের ঘোরাঘুরি - হাটে বাজারে , বন্ধু সন্দর্শনে সেখানে আমার গাড়ির টিকিটি বাঁধা আছে তিরিশ বা বড়জোর পঞ্চাশ মাইল বেগে । প্রয়াত ভাস্করদার ( ভাস্কর দত্ত , সুনীলদার অভিন্ন হৃদয় বন্ধু) পুত্র অর্ণবের বাড়ি থেকে কিছু সঞ্চিত বই সংগ্রহের জন্য উত্তর লন্ডনের স্টোক নিউইংটন গেলাম গত রবিবার - এককালের সেই বিখ্যাত ওয়েস্টওয়ে আকীর্ণ হয়ে আছে অজস্র ক্যামেরায়, ওয়েম্বলি, হ্যামারস্মিথ থেকে কিংস ক্রস ছাড়িয়ে গাড়ি চলে ধীরে মন্দ গতিতে, আইন বাঁচিয়ে ।
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাকাদামাটির হাফলাইফ - ইট পাথরের জীবন - ইমানুল হক
১৫ জুন ২০২৪ | ২০ বার পঠিতমায়ের সঙ্গে ছেলের প্রবল মতাদর্শগত অমিল। অথচ এই অবিবাহিত ছেলেকে ঘিরেই মায়ের গোপন আবেগ। ভালোবাসা। ছেলে সূর্যকুমার যখন সংসার ভেঙ্গে ভাগ হয়ে যাচ্ছে, মানতে না পেরে এবং অন্যান্য কারণে আত্মহত্যা করে। আমাদের ছোটবেলায় অভাবের জ্বালায় সংসার চালাতে না পেরে পুরুষ বা নারীর আত্মহত্যার চেষ্টা দেখেছি। তবে এক 'মুসলিম' তরুণীর প্রেমে এক 'হিন্দু' তরুণের আত্মহত্যা গ্রামে খুব আলোড়ন তোলে।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালদিলদার নগর ৪ - Aditi Dasgupta
১৪ জুন ২০২৪ | ১৩৮ বার পঠিতঘটমান বর্তমান ঘটেনাতো পিছনের কথামুখ ভুলি। দিলদরিয়াতে নেমে একে একে খুলে যায় -- এ ‘আমির’ আবরণ গুলি।।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালকিষেণজি মৃত্যু রহস্য - পর্ব ১৩ - বিতনু চট্টোপাধ্যায়
১৪ জুন ২০২৪ | ১২৮ বার পঠিতমিনিট খানেক বাদে এসপি ফোন ছেড়ে বললেন, ‘‘কিছু হয়নি তেমন। ইলেকট্রিকের তার ছিঁড়ে পড়েছে কনভয়ে পুলিশের গাড়ির ওপর। তাতেই টাল সামলাতে না পেরে পুলিশের গাড়ি রাস্তার ধারে পড়ে গিয়েছে।’’ এসপির কথায় আশ্বস্ত হলেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফোন ছেড়ে প্রভীণ কুমার জানালেন, ‘‘স্যার, ব্লাস্ট হয়েছে। ব্লাস্টে ইলেকট্রিক তার ছিঁড়ে মাটিতে পড়েছে। জোরে আওয়াজ হয়েছে, বড় ব্লাস্ট ছাড়া তা হতে পারে না।’’
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজানিট কেলেঙ্কারি - পর্দা ফাঁস - ভিডিওগুরু
১৪ জুন ২০২৪ | ৩৭০ বার পঠিতনিট কেলেঙ্কারি নিয়ে নিয়ে বাংলা মিডিয়া এখনও মোটামুটি চুপচাপ, যেটুকু না বললে নয়, সেইটুকু বলছে। যদিও এরকম হবার সম্ভাবনা আছে, যে, নিটই স্বাধীন ভারতবর্ষের বৃহত্তম কেলেঙ্কারি। হ্যাঁ, আদালতের রায়ের পরেও ব্যাপারটা বদলায় না। কিন্তু মূলধারার মিডিয়ার হাতে ছেড়ে দেব বলে তো আমরা কাজ করছিনা। এই ভিডিওটা দেখুন, বিশদে পুরোটা বলা আছে।
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাপ্রথম ব্ল্যাক হোল - সহস্রলোচন শর্মা
১৩ জুন ২০২৪ | ১৪৩ বার পঠিতব্ল্যাক হোল?! ননসেন্স! বাস্তব জগতে ব্ল্যাক হোল বলে কোনও কিছুর অস্তিত্বই নেই। অস্তিত্ব থাকতে পারে না। এটা নেহাতই গণিতের একটা ফসল মাত্র। ‘ব্ল্যাক হোল’ হলো তাত্ত্বিক পদার্থবিদদের উর্বর মস্তিষ্ক প্রসূত এক কল্পনা বিলাস। এই কল্পনার না আছে কোনও বাস্তব ভিত্তি না আছে কোনও বাস্তব প্রমাণ। এমনটাই মনে করতেন সেই সময়ের অধিকাংশ বিজ্ঞানীরা। কেউ কেউ যদিও ব্ল্যাক হোলের অস্তিত্বের উপর ভরসা রাখতেন। তবে সেই সময়ে, ঈশ্বরে বিশ্বাস করার মতোই ব্ল্যাক হোলে বিশ্বাস করাও ছিল প্রমাণহীন একটা ধারণা মাত্র।
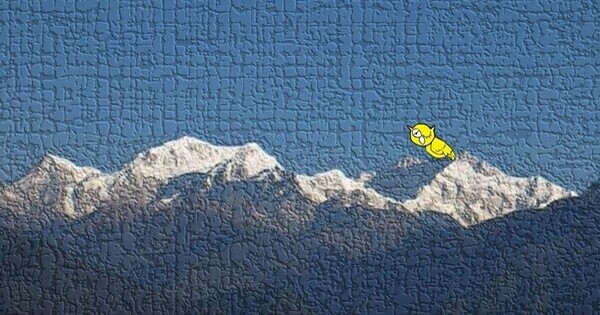 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাভ্রান্তিপর্বত শান্তিতীর্থ - নন্দিনী সেনগুপ্ত
১৩ জুন ২০২৪ | ১২৩ বার পঠিতচলতি বছরে মে মাসের প্রথম সপ্তাহে উত্তরাখণ্ডে পাঁচ জন মানুষের মৃত্যু ঘটেছে দাবানলে। প্রশ্ন উঠতে পারে যে দাবানলে মানুষ মরল কী ভাবে? কারণ দাবানল অরণ্যে হয়। তাহলে কি দাবানল এত বিধ্বংসী আকার ধারণ করেছে যে সেই আগুন ছড়িয়ে পড়েছে অরণ্যের পাশের জনপদে? এক্ষেত্রে সম্ভাব্য কারণ বলা হচ্ছে মানুষ দাবানল নেভাবার চেষ্টা করতে গিয়ে ঘটেছে এই ঘটনা। পাহাড়ে আদিবাসীদের একটা বড় অংশের মানুষের কাছে বৃক্ষ এবং অরণ্যের মহিমা দেবতার মত। পরিবেশবিজ্ঞান বইয়ের পাতা উল্টে শেখে না তারা। জন্ম থেকেই মানুষ প্রকৃতির হাত ধরে বাঁচে সেখানে, ফলে নাগরিক সভ্যতার বৃত্তের বাইরের মানুষ বৃক্ষদেবতা তথা অরণ্যকে বাঁচাবার চেষ্টা করবে, এমন ঘটনা নতুন নয়।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালতোমার বাস কোথা যে... - ৬ - Nirmalya Nag
১৩ জুন ২০২৪ | ২৭০ বার পঠিতফোনে কথা বন্ধ করল ইন্দ্রনীল, জামার পকেটে মোবাইল রেখে দুজনের দিকে একবার তাকাল। তারপর খামটা এগিয়ে দিল বিনীতার দিকে, সে ওটা হাতে নিল। ইন্দ্রনীল দেখল অরুণাভর বই বুকের ওপর খোলা, চোখ তারই দিকে। “সার্জারি ভালই হয়েছে। কিন্তু কন্ডিশন ভাল নয়। টিউমারটা ম্যালিগন্যান্ট,” কথা বলতে বলতেই ডাক্তার দেখল অরুণাভর চোখ বইয়ের দিকে ঘুরল। “আমি অকারণ আশা দিতে চাই না। মেটাস্টেসিস শুরু হয়েছে, মানে ছড়িয়ে গেছে রোগ, স্টেজ ফোর।” বিনীতা বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল ইন্দ্রনীলের দিকে, তারপর দেখল তার স্বামীর দিকে। তার চোখ বইয়ের পাতায়, তবে মন কোথায় বলা কঠিন।
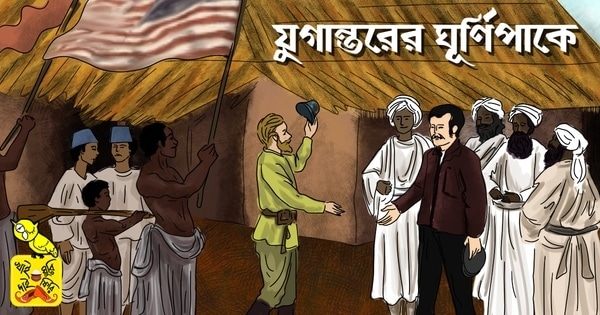 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাডেভিড লিভিংস্টোনের খোঁজে-১৪২ - হেনরি মর্টন স্ট্যানলে
১৩ জুন ২০২৪ | ৪৩ বার পঠিতআমাদের শিবির থেকে, আমেরিকান কনসালের কাছে চিঠি দিয়ে তিনজনকে জাঞ্জিবারে পাঠিয়েছিলাম, সেই সঙ্গে 'হেরাল্ড'-এর কাছে টেলিগ্রাফ পাঠানোর জন্যও। রাজদূতকে অনুরোধ করেছিলাম যে তিনি যেন একটা-দুটো ছোট বাক্স ভরে কিছুমিছু বিলাসদ্রব্য দিয়ে লোকদের ফেরত পাঠান যা ক্ষুধার্ত, জীর্ণ, ছ্যাতলাধরা মানুষজন তারিফ কুড়াবে। বার্তাবাহকদের বৃষ্টি- অনাবৃষ্টি, নদী- বন্যা কোনো কিছুর জন্যই থামতে বারণ করা হয়েছিল - যাতে তারা তাড়াহুড়ো করল না আর তারা উপকূলে পৌঁছানোর আগেই আমরা তাদের ধরে ফেললাম এমন ঘটনা না ঘটে। প্রবল উৎসাহে "ইনশাআল্লাহ, বানা" বলে তারা রওনা দিল।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালসিঙ্গুরের পরের স্টেশন - সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায়
১৩ জুন ২০২৪ | ১০৩৫ বার পঠিতসিঙ্গুরের পরের স্টেশন কামারকুন্ডুতে, প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান শুনলাম, এক হকারকে আরপিএফ গুঁতো মেরে ট্রেনে থেকে ফেলে দিয়ে মেরে ফেলেছে বলে অভিযোগ। কেন্দ্রীয় বাহিনী। পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত এলাকায়, কিছুদিন আগেই বিএসএফ একজনকে গুলি করে মেরে ফেলেছিল বলে অভিযোগ। কেন্দ্রীয় বাহিনী। তাদের দাপাদাপি সীমান্ত ছাড়িয়ে অনেক দূর পর্যন্ত। কান পাতলেই অভিযোগ শুনতে পাওয়া যায়। তাদের দাপাদাপি রেলে। কান পাতলেই শুনতে পাবেন অত্যাচারের অভিযোগ। বাঙালিদের তুলে হিন্দুস্তানিদের বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে হকার হিসেবে, স্টেশনের স্থায়ী স্টলগুলোতে হিন্দিভাষীদের অস্বাভাবিক বাড়বৃদ্ধি।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালধ্যান এবং স্নায়ুবিজ্ঞান - অরিন
১২ জুন ২০২৪ | ৪৩৭ বার পঠিতজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মনোনিবেশ এবং ধ্যান ব্যাপারটির অপরিসীম তাৎপর্য। ধ্যান ব্যাপারটিকে ধর্ম, রীতিনীতি বা মনোবিজ্ঞান থেকে একটু সরিয়ে দেখা যাক। একটা প্রশ্ন ওঠা খুবই স্বাভাবিক: যে ধ্যান করলে মনের "গভীরে" হয় কি? যদি সত্যি কিছু হয়, তাকে জানা যাবে কোন উপায়ে? কোনটা বিজ্ঞান আর কোনটা নয়? এই প্রশ্নগুলোকে কেন্দ্র করে আমাদের মস্তিষ্ক, এবং চেতনার একটা আকর্ষণীয় দিক নিয়ে আলোচনার ব্যাপার রয়েছে। বিশেষ করে, ধ্যান বিষয়টিকে কেন্দ্র করে স্নায়ুবিজ্ঞান (নাকি স্নায়ুশাস্ত্র) ও কম্পিউটার বিজ্ঞানের মেলবন্ধনে চিন্তাভাবনার একটি নতুন দিক উন্মোচিত হচ্ছে।
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাখাদ্য এবং খাদ্য ফসলের দূষণ একটি নীরব ঘাতক - সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপ ও সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ন সমাধান - শ্যামল অধিকারী
১২ জুন ২০২৪ | ২৮৯ বার পঠিতFSSAI (ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া) এর চরম ব্যর্থতা। খাদ্যদ্রব্যের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে এবং রাসায়নিক পেস্টিসাইড নিয়ন্ত্রণ করতে FSSAI সম্পূর্ণ ব্যর্থ। দায়ের করা একটি পিটিশনে বলা হয়েছে যে কীটনাশক যুক্ত খাবারের ব্যবহার সারাদেশে ক্যান্সার রোগের প্রধান কারণ হয়ে উঠেছে এবং তাতে মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে। কীটনাশক এবং ক্যান্সারের মধ্যে একটি সরাসরি বৈজ্ঞানিক সম্পর্ক রয়েছে। ফলে কীটনাশক যুক্ত খাবার, তার ব্যবহার, অতিব্যবহার এক বিরাট চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আবেদনকারী সারা দেশ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন যা দেখায় যে কীটনাশকের কারণে মৃত্যুর সংখ্যা বেশি হচ্ছে। সিনিয়র আইনজীবী অনিথা শেনয়, আবেদনকারী অ্যাডভোকেট আকাশ বশিষ্ঠের পক্ষে উপস্থিত হয়ে সুপ্রিম কোর্টকে জানালেন। পাশাপাশি পিটিশনে ক্যালসিয়াম কার্বাইড এর মতো রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে ফল কৃত্রিমভাবে পাকানো, আপেলের মত ফলগুলির রং বা আবরণ প্যারাফিন, শেলাক এবং পলিথিনের মত উপাদান দিয়ে তৈরি মোম দিয়ে পলিশিংয়ের বিষয়টিও উল্লেখ করা হয়। এছাড়া ডাল এবং খাদ্যশস্যে কৃত্রিম রং ব্যবহারের কথাও উল্লেখ করা হয়। ভারতের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বে সুপ্রিম কোর্টের এক বেঞ্চ 17 মে, 2024 পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক, কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা ও মান অথরিটি অফ ইন্ডিয়াকে (FSSAI) নোটিশ জারি করেছে এবং তাদের প্রতিক্রিয়া চেয়েছে।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালমোদি কি আদৌ বারানসীতে জিতেছেন? - সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায়
১২ জুন ২০২৪ | ৩০৯ বার পঠিতমোদি কি আদৌ বারানসীতে জিতেছেন? ফলাফল বেরিয়ে যাবার পর এই প্রশ্ন কেন? কারণ, অন্য কেউ না, বিজেপির নেতারাই প্রশ্নটা তুলছেন। গোপন কিছু না। আস্ত সাক্ষাৎকার বেরিয়েছে। কিন্তু খুব সম্ভবত আপনি দেখেননি, কারণ মিডিয়া দেখায়নি। বা যৎসামান্য দেখিয়েছে। ওদিকে ব্যাপারটা কিন্তু বিস্ফোরক। তাই আমরাই ভিডিও সমেত জিনিসটা সামনে নিয়ে এলাম। আমাদের চ্যানেল এখনও পুরোদস্তুর তৈরি না। কিন্তু এইসব জিনিস এলে এখনও সঞ্চালকরা তৈরি না বলে তো থেমে থাকা যায়না। তাই করে ফেলা হল। কেন করে ফেলতে হল, সে দেখলেই বুঝতে পারবেন।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালদোলজ্যোৎস্নায় শুশুনিয়ায় - ১৮ - সমরেশ মুখার্জী
১২ জুন ২০২৪ | ৪৯ বার পঠিতআশির দশকে যাদবপুরের কয়েকটি ছাত্রছাত্রী শুশুনিয়া পাহাড়ে গেছে শৈলারোহণ অভ্যাস করতে - সেই ভিত্তিতে এই আখ্যান … যতই মুড অফ থাকুক, কেউ লুজ বল দিলে ছক্কা মারার জন্য সুমনের মন নিশপিশ করে। ভাবলেশহীন মুখে বলে, "তোর সাথে একা গল্প করতে আমার ভয় করে।" কোমরে দু হাত দিয়ে তুলি লড়াকু ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে বলে, "ভয় করে! কেন? আমি কী কামড়ে দেবো তোকে?"
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালচললুম ঈর্ষাহীন দেবীর গৃহে (সমাপ্ত) - সমরেশ মুখার্জী
১১ জুন ২০২৪ | ২৫১ বার পঠিত"একা বেড়ানোর আনন্দে" - এই সিরিজে আসবে ভারতের কিছু জায়গায় একাকী ভ্রমণের অভিজ্ঞতা। এটি পর্ব - ২৮ … দুবার একই ভুল করে একটি জনশ্রুতির মর্মার্থ উপলব্ধি করেছি কাঁপতে কাঁপতে - ছাগল দিয়ে লাঙ্গল দেওয়া গেলে চাষা বলদ কিনতো না। সেবার উত্তরাখণ্ড ভ্রমণে পঞ্চকেদারের দুটি কেদারে গেছিলাম। একাকী যোশিমঠ থেকে কল্পেশ্বর। ছ জনের দলে তুঙ্গনাথ। দলটি হয়েছিল গুপ্তকাশীতে আলাপ পাঁচটি উত্তরপ্রদেশের তরুণের সাথে। তুঙ্গনাথ, দেওরিয়া তালে দুটি রাত কাটিয়ে উখিমঠ থেকে ওরা হরিদ্বার চলে যেতে আবার আমি একা
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাহাসপাতালের ডায়েরি - পারমিতা চৌধুরি
১০ জুন ২০২৪ | ৫৮৬ বার পঠিতএ বছর চৈত্রের শুরু থেকেই ঝলসে দেওয়া শুকনো গরম। সেই গরমে sskm এর এক একটা লাইনে তিন ঘন্টা দাঁড়িয়ে নারী পুরুষ। মেয়েরা এখানে সংখ্যাগুরু। সংসারের যাবতীয় কাজ ভোর রাতে উঠে সামলে তারা চলে আসে। কখনো নিজের জন্য, কখনো সন্তানের জন্য। এমনকি এমন মেয়ের দেখা পেয়েছি যে sskm চেনে হাতের তালুর মত আর তার হাত ধরে প্রথমবারের জন্য ডাক্তার দেখাতে এসেছে তার স্বামী। মেয়েরা না কি রাস্তা পেরোতে পারে না
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালকাটাকুটি - সমরেশ মুখার্জী
১০ জুন ২০২৪ | ১০১ বার পঠিতএটা আজই আমার পাতায় পোষ্টিত “টুনটুন মুনটুন”- লেখার প্রলম্বিত পুনশ্চঃ
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালটুনটুন মুনটুন - সমরেশ মুখার্জী
১০ জুন ২০২৪ | ২১০ বার পঠিতকঠোরভাবে প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য - দেশব্যাপী পঞ্চবার্ষিকী যাত্রাপালা সদ্যসমাপ্ত হয়েছে। বিগত কয়েক হপ্তা ধরে তাই নিয়ে এন্তার কূটকচা৯ দেখেশুনে মনপ্রাণ ভারাক্রান্ত। কিছু মাস বাদে ঐ রঙ্গপালাই চলবে আরো কিছু প্রদেশে আঞ্চলিক পর্যায়ে। তার মাঝে একটু হালকা হতে লিখলুম এই চিরন্তন লীলাপ্রসঙ্গ … তবে তরল আঙ্গিকে
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাদুয়ারসিনি - নরেশ জানা
০৯ জুন ২০২৪ | ২৩৭ বার পঠিতরাস্তায় নেমেই ঘড়ির কাঁটায় নজর দিয়ে দেখে নিয়েছি বেলা তখন দশটা বেজে পনেরো। ঝাড়খন্ড আর বাংলার আকাশ থেকে তখনও ঘূর্ণাবর্তের ছায়া কাটেনি বটে কিন্তু এখন এই মুহূর্তে সোনার মত রোদ গলে পড়ছে। গুগল ট্র্যাকার দেখে ঝিলমিল আর রাগিণী আমাকে জানালো আমাদের হাঁটতে হবে এক কিলোমিটার পথ। মৃত্যুঞ্জয় গাড়িটা নিয়ে এগিয়ে গেছে, গীয়ার নিউট্রাল করে শব্দহীন গাড়ি নেমে গেছে সুন্দরী দুয়ারসিনির পথে। আমাদের সাথেও রয়েছে চার সুন্দরী। রুশতি আজ জিন্স্ পরেছেন। নীল ফেডেড জিন্সের ওপর লাল আর কালো স্ট্রাইপ দেওয়া সাদা শার্ট। মেয়ে রাগিণী আজ পুরোপুরি কালো পোশাকের আশ্রয় নিয়েছে। স্লিভলেস ঝালর দেওয়া কালো টপ আর পালাজো। রিয়ানের আজ কমলা আশ্রয়। কলার দেওয়া হাঁটু ছাড়ানো কুর্তি আড়াল করেছে কালো চোস্তা পাজামাকে। ঝিলমিল একটা মেরুন পাজামার ওপর কালো টি শার্ট চড়িয়েছে।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালদোলজ্যোৎস্নায় শুশুনিয়ায় - ১৭ - সমরেশ মুখার্জী
০৯ জুন ২০২৪ | ৬৬ বার পঠিতআশির দশকে যাদবপুরের কয়েকটি ছাত্রছাত্রী শুশুনিয়া পাহাড়ে গেছে শৈলারোহণ অভ্যাস করতে - সেই ভিত্তিতে এই আখ্যান …একটা অবুঝ অভিমান দলা পাকিয়ে উঠছে সুমনের মনে। মলয়দা রেশনিং করে খেতে বলা সত্ত্বেও ওরা কিছুটা জল বাঁচিয়ে রাখতে পারলো না ওদের জন্য? এই ফেলো ফিলিংস নিয়ে এরা পাহাড়ে যাবে?
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাএমনি এমনি মারি - রমিত চট্টোপাধ্যায়
০৮ জুন ২০২৪ | ৫৬১ বার পঠিত বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাস্লোভাকিয়া ৫ - হীরেন সিংহরায়
০৮ জুন ২০২৪ | ৪৬৯ বার পঠিত হরিদাস পাল
হরিদাস পালচললুম ঈর্ষাহীন দেবীর গৃহে - ২ - সমরেশ মুখার্জী
০৮ জুন ২০২৪ | ১৭১ বার পঠিত"একা বেড়ানোর আনন্দে" - এই সিরিজে আসবে ভারতের কিছু জায়গায় একাকী ভ্রমণের অভিজ্ঞতা। এটি পর্ব - ২৭ … পরিচিত সঙ্গীর সাথে হপ্তা দুয়েক অবধি ভ্রমণ ঠিক আছে। তার বেশী হলে নানা কারণে ছানা কাটতে শুরু করে। কিন্তু দু মাসের একাকী ভ্রমণেও কখনো সঙ্গীহীনতার চাপ অনুভব করিনি। সেলফ ড্রাইভ করে বেড়াতে গেলে বাস্তবিক কারণে সাথে একজন থাকলে সুবিধা হয়। কারণ পথে গাড়ি খারাপ হতেই পারে। জনবাহনে গেলে সে প্রয়োজন নেই। একাকী ভ্রমণে সঙ্গীর অভাব বোধ না করলেও চলার পথে স্থানীয় মানুষের সাথে গল্পগুজব করতে ভালোই লাগে। যাদের সাথে আর কখনো দেখা হবেনা তাদের সাথে ক্ষণিকের আলাপ স্মৃতিতে রয়ে যায় বহুদিন
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাবিপ্লবের আগুন - পর্ব আট - কিশোর ঘোষাল
০৮ জুন ২০২৪ | ১৩০ বার পঠিতপ্রথম দিন আলাপের সময়েই এই দলটি তার কাছে বিদ্রোহের মন্ত্র জানতে চেয়েছিল। সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে একত্রে লড়ে যাওয়ার শপথ নিয়েছিল। বলেছিল ভল্লাদা তুমি একা, তাই ওরা তোমাকে এভাবে চূড়ান্ত হেনস্থা করতে পেরেছে। তোমার ওপর ঘটে যাওয়া এই অপমানের শোধ তুলব আমরা সবাই মিলে। ভল্লা মনে মনে হেসেছিল। একটু বিদ্রূপের সুরে গম্ভীর মুখে ভল্লা বলেছিল, “খাওয়া, ঘুমোনো আর হাগতে-পাদতে-মুততে যাওয়া ছাড়া আর কী পারিস? ছুটতে পারিস? লাফাতে পারিস? গাছে উঠতে পারিস? সাঁতার কাটতে পারিস? অস্ত্র চালাতে পারিস কিনা জানতে চাইলাম না। জানি, ও জিনিষ তোরা কোনদিন হাতেও ধরিসনি”।
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাপরিযায়ী শ্রমিক, মহিলা ভোটার আর ২০২৪ নির্বাচনের কিছু গণিত - সুদীপ্ত পাল
০৮ জুন ২০২৪ | ৩২৯ বার পঠিতমঙ্গলসূত্র, মুসলিম, মাটন, মাচ্ছি, মোষ, মুজরা- এসবের মাঝে যে দুটো ম-এর কাহিনী চাপা পড়ে গেছে সেটা হল মহিলা ভোটার আর মাইগ্রেন্ট লেবারার। ২০২৪ এর লোকসভা নির্বাচনের প্রথম দুই দফায় যে বিষয়টা নজর কেড়েছিল সেটা ছিল ভোট শতাংশ কমে যাওয়া। নির্বাচনের শেষের দিকে যেটা নজর কেড়েছে সেটা হল পুরুষদের চেয়ে নারীদের বেশিমাত্রায় অংশগ্রহণ। নারীদের মধ্যে অতিরিক্ত ভোটদানের হার বিশেষভাবে দেখা গেছে বিহার, পূর্ব উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলায় এবং ঝাড়খণ্ডে। সবচেয়ে লক্ষণীয় হল বিহার। বিহারে প্রথম দফায় নারীদের ভোট শতাংশ পুরুষের চেয়ে কম ছিল। দ্বিতীয় দফা থেকে বাড়তে শুরু করে। বিহারে যেটা কমেছে সেটা হল পুরুষদের ভোটদানের হার- এটা ৫৫.১% থেকে ৫৩.৩% এ নেমে এসেছে। মহিলাদের ভোটদানের হার ৫৯.৪% যা ২০১৯এর প্রায় সমান।
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাকাদামাটির হাফলাইফ - ইট পাথরের জীবন - ইমানুল হক
০৮ জুন ২০২৪ | ২১২ বার পঠিতহিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ মুরগি পালন করতেন না। তাঁদের ঘরের মেয়েরা হাঁস পালন করতেন। কোনও হিন্দু বাড়িতেই মুরগি ঘরে রান্না করা যেত না। ফিস্টিতে খেতে হতো। মুরগিকে বলা হতো রামপাখি। মুরগির ডিমকে রামফল। জ্বর সর্দি হলে শরীর দুর্বল হলে প্রেসার লো হলে গ্রামের ডাক্তার মুরগির হাফ বয়েল ডিম খেতে নিদান দিতেন। তখন মুসলিম বাড়িতে গিয়ে মুরগির ডিম কিনে আনতে যেতো। এখন তো মুরগির মাংস জলভাত পোল্ট্রির কল্যাণে। এই পোল্ট্রি আমাদের গ্রামে আসে বামফ্রন্টের বেকার ভাতা দেওয়ার কল্যাণে। বেকার ভাতা পেতেন তিনজন। তিনজনই কংগ্রেসি। এঁরা ম্যাট্রিক পাস করে কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রে নাম লিখিয়েছিলেন। নাসির চাচা ও সালাম চাচা ছিলেন উদ্যোগী মানুষ। দুজনেই আমার খুব পছন্দের মানুষ। তাঁদের রাজনীতি আমাদের পরিবারের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপনে কোনও বাধা হয়নি। বামপন্থী রাজনীতির কারণে ২০০৯ থেকে আমাদের পরিবারকে বয়কট করা হলেও সালাম চাচা, ধনা চাচা ও মাদু চাচা নিয়মিত যোগাযোগ রেখেছেন। এসেছেন। আর এসেছেন ব্রাহ্মণ সন্তান পীরে কাকা। সালাম চাচা ও নাসির চাচা কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্র থেকে বামফ্রন্ট সরকারের দেওয়া ঋণ নিয়ে গ্রামে প্রথম পোল্ট্রি করলেন। গ্রামের বাইরে মাঠে। তখন ঘরোয়া মুরগির মাংসের দাম ২০ টাকা। ছাগলের মাংসের নাম তখন মাটন হয়নি। দশ টাকা কিলো। এবার পোল্ট্রি এসে দাম হল ১৫ টাকা কেজি।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালএকটি টি-শার্ট - মোহাম্মদ কাজী মামুন
০৮ জুন ২০২৪ | ১৮১ বার পঠিতপুলসিরাত পার হয়ে যখন শেষমেষ তারা ঢুকলো অফিসটাতে, তখন দেখা গেল সেলিম ভিজলেও তার বসের মত কাকভেজা হয়নি, ফ্যানের বাতাসে একটুখানি বসলেই চলছে। ওদিকে বসের সামনে মেলে ধরা হয়েছে দীপুর টি-শার্টটা।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালবহিরাগত শিল্পী - Mani Sankar Biswas
০৭ জুন ২০২৪ | ৯৭ বার পঠিতবহিরাগত শিল্পী হেনরি ডারগার
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালকিষেণজি মৃত্যু রহস্য - পর্ব ১২ - বিতনু চট্টোপাধ্যায়
০৭ জুন ২০২৪ | ১৯৬ বার পঠিত‘বুদ্ধদেববাবুর কনভয়ে ব্লাস্ট হয়েছে? একটা চ্যানেল দেখাচ্ছে।’ অফিস থেকে আসা এই এক লাইনের বার্তাই তখন যথেষ্ট ছিল। ড্রাইভারকে গাড়ি ঘোরাতে বলে সঙ্গে সঙ্গে ফোন করলাম মুখ্যমন্ত্রীর আপ্ত সহায়ক জয়দীপ মুখার্জিকে। ‘বুদ্ধদেববাবুর কনভয়ে ব্লাস্ট হয়েছে?’ ‘কিছু একটা হয়েছে। তবে ব্লাস্ট না। এসপি বলছে, ইলেকট্রিক ওভারহেড তার ছিঁড়ে একটা পুলিশের গাড়ির ওপর পড়েছে। তাতে একটু আগুন ধরে যায়। টাল সামলাতে না পেরে গাড়িটা উল্টে গিয়েছে। তাতে তিন-চারজন পুলিশ ইনজিওরড। তবে সিএমের কনভয়ে না, এটা ঘটেছে রামবিলাস পাসোয়ানের কনভয়ে।’
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালমহম্মদ সেলিম এবং লক্ষ্মীর ভাণ্ডার - সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায়
০৬ জুন ২০২৪ | ৮৮০ বার পঠিতমহম্মদ সেলিম বহু ক্ষেত্রেই সঠিক কথা বলে থাকেন। এবারও বলেছেন। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নিয়ে তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, "কেউ কেউ স্বঘোষিত বিপ্লবী আছে, তাদের আমরা বলি ফেসবুকে বেশি বিপ্লবীয়ানা করবেননা। কিন্তু করে। এখানে এমন একটাও সিপিএমের কাছ থেকে এক্সপেক্ট করতে পারোনা, যে, মহিলাদের সম্পর্কে বা এ ধরণের ভাতা সম্পর্কে অফিশিয়ালি ডিনাউন্স করছে। কেন করবে? আমরা আমাদের বামপন্থী আন্দোলন মানে হচ্ছে, গোট বিশ্বে আমরা চাই, সরকার ক্ষতিপূরণ হিসেবে, মানুষের যে অধিকার দিতে পারছেনা, তাকে কিছুটা অন্তত সাবসিডাইজ করবে। আর বাকি যারা এগুলো নিয়ে কটাক্ষ করছেন, তাঁরা বামপন্থী নন, তাঁরা হতে পারেন সমর্থক, আমাদের দায় আমাদের কথা তাঁদের কাছে নিয়ে যাওয়া, আমাদের মাধ্যমগুলো দিয়ে, সরাসরি তাঁদের কাছে গিয়ে। কেউ কেউ উগ্র সমর্থক আছেন, তাঁদের আমরা সমর্থক থাকতে বলব, উগ্রতা কমাতে বলব।" (শুনে শুনে লেখা, মোটামুটি হুবহু উদ্ধৃতি)।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালশিক্ষা না ভিক্ষা? - Anirban M
০৬ জুন ২০২৪ | ৪৮৫ বার পঠিতবাংলায় যে তৃণমূল প্রার্থীরা জিতলেন তাঁরা কী হেরে যাওয়া বাম প্রার্থীদের থেকে কম শিক্ষিত? এবং দেশে যে বামেরা জিতলেন তাঁরা কী বাংলার তৃণমূল বা বাম প্রার্থীদের থেকে কম বা বেশি শিক্ষিত? এই দুটি প্রশ্নের উত্তর বোঝার চেষ্টা তথ্যের ওপর ভিত্তি করে।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালহাঁটতে হাঁটতে - দ
০৬ জুন ২০২৪ | ২৫০ বার পঠিতঝলমলে সোশ্যাল মিডিয়া আর স্মার্টসিটির বাইরে কবে থেকে যেন হেঁটেই চলেছে আরেকটা ভারত। এতদিনে তাদের অন্তত নামটুকু নথিবদ্ধ থাকার কথা ছিল সরকারের কাছে। কথা ছিল, কিন্তু নেই আসলে, আর সেজন্য আমরা ন্যুনতম লজ্জিতও নই, প্রশ্নও করি না কেন অভিবাসী শ্রমিকদের তালিকা নেই সরকারের কাছে? কেন স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরেও গ্রামীণ মেয়েদের এত হাঁটতে হবে শুধুমাত্র জলের জন্য? বইটা আমাদের জ্বলন্ত এই প্রশ্নগুলোর মুখোমুখী দাঁড় করিয়ে দেয়। মনে করিয়ে দেয় ‘সুনাগরিক’এর দায়িত্ব পালন করি নি আমরাও।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালচললুম ঈর্ষাহীন দেবীর গৃহে - ১ - সমরেশ মুখার্জী
০৬ জুন ২০২৪ | ১৩৭ বার পঠিত"একা বেড়ানোর আনন্দে" - এই সিরিজে আসবে ভারতের কিছু জায়গায় একাকী ভ্রমণের অভিজ্ঞতা। এটি পর্ব - ২৬ … এই সিরিজের ৪নং পর্বে জনৈক নীল ২১.১০.২৩ লিখেছিলেন - “অনসূয়া দেবী যাত্রার কথা লিখবেন না?” বলেছিলাম - “লিখবো। সেও বেশ আনন্দময় অভিজ্ঞতা”। আরো নানা বিষয়ে লিখতে গিয়ে সময় হয়নি। এতোদিনে নীলের অনুরোধ রাখতে পারলাম। তবে আমার ছড়িয়ে ফেলা স্বভাব অনুযায়ী এই যাত্রা পথেও আসবে কিছু পার্শ্বপ্রসঙ্গ
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালহিন্দু মুসলমান -- একটি অ-জনপ্রিয় আলোচনা - Partha Banerjee
০৬ জুন ২০২৪ | ২৯২ বার পঠিতউগ্র সাম্প্রদায়িক ও নারীবিদ্বেষী হিন্দুত্ববাদী বিজেপি-আরএসএসের বিরোধিতার সঙ্গে সঙ্গে উগ্র সাম্প্রদায়িক ও নারীবিদ্বেষী এই মুসলমান শ্রেণীর সমান বিরোধিতা আমাদের করতে হবে। না হলে আমাদের কোনো বিশ্বাসযোগ্যতা সমাজে থাকবে না।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালতোমার বাস কোথা যে...-৫ - Nirmalya Nag
০৬ জুন ২০২৪ | ৩৫২ বার পঠিতডাক্তারের চেম্বারের দরজা ঠেলে ঢুকে বিনীতা দেখল ব্যাগ গোছাচ্ছে ইন্দ্রনীল। বিনীতাকে দেখে একটু অবাক হল সে। “কিছু বলবেন, ম্যাডাম?” “আপনি বললেন প্রতিটা দিনই ইমপরট্যান্ট। ওর কন্ডিশন ঠিক কতটা খারাপ?” “আরে না না। শুনুন, এই কন্ডিশন থেকে লোকে সুস্থ হয়েছে এমন অনেক এক্সাম্পল আছে।” “তার মানে কন্ডিশন খারাপ। কতটা? ও কি–” বিনীতার কথা থামিয়ে দিল ইন্দ্রনীল। “শুনুন, যা যা করার সব করা হবে। বললাম না প্রথমে সার্জারি, তারপর–” এবার ইন্দ্রনীলকে থামাল বিনীতা। “ও সব আপনি আগেই বলেছেন। এখন ক্লিয়ারলি বলুন, ও কি টার্মিনাল পেশেন্ট?” “দেখুন ম্যাডাম…” “আমি যথেষ্ট স্ট্রং, আপনি বলুন।” ইন্দ্রনীল চুপ করে থাকে।
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজা‘ঘরের শত্রু বিভীষণ’ মাইক্রোপ্লাস্টিক - স্বাতী রায়
০৫ জুন ২০২৪ | ৫৫০ বার পঠিতশত্রুর নাম হল প্লাস্টিক। এমনিতে প্রচণ্ড দরকারি জিনিস। কিসে না লাগে! কিন্তু সমস্যা এইটাই যে প্লাস্টিক বলতে আমরা যে বিভিন্ন ধরণের রাসায়নিক দ্রব্য বুঝি, তাদের সবকটিকে পুনর্ব্যবহারযোগ্য করার কোন পকেটসই সুবিধাজনক পরিবেশ বান্ধব উপায় মেলে না। আবার সেটা এমনি ফেলে রাখলে প্রকৃতিতে মিশে যেতে অতি দীর্ঘ সময় লাগে। আর ততদিনে ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে সেটা ম্যাক্রো-প্লাস্টিক মেসো-প্লাস্টিক, মাইক্রো-প্লাস্টিক ইত্যাদি বিভিন্ন আকারের চেহারা নেয়। ম্যাক্রোপ্লাস্টিক হল ২.৫ সেমির থেকেও দৈর্ঘে বা প্রস্থে বড় যে কোন প্লাস্টিকের টুকরো। ৫ মিমি – ২.৫ সেমি অবধি টুকরোকে বলে মেসো-প্লাস্টিক। আর মাইক্রোপ্লাস্টিক বলা হও ১ মাইক্রো মিলিমিটার থেকে ৫ মিলিমিটারের সাইজের প্লাস্টিকের কণা। এই মাইক্রোপ্লাস্টিক নিয়েই আজকের কথা। কারণ আজকের দিনে এরা জলে স্থলে বাতাসে সর্বত্র ভেসে বেড়াচ্ছে।
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাভ্রমণের বিষ - প্রতিভা সরকার
০৫ জুন ২০২৪ | ৫৯৭ বার পঠিতআমি বিদ্যাকে শুধোই, শুধু পাহাড়ের কি কোনো একক দেবতা নেই, যিনি তাকে রক্ষা করতে পারেন লাগাতার ধ্বংস আর নির্বিচার আক্রমণ থেকে? তাকে বলি, সমস্ত পাহাড়ের রাণী যে হিমাচল প্রদেশ তার চেহারা দিনের দিনের পর দিন যেভাবে কুৎসিত হয়ে উঠছে, তা কল্পনাতীত। পাঞ্জাব পেরিয়ে হিমাচলের সীমানায় ঢুকলেই শুধু উন্নয়ন, নির্মাণ, জেসিপি আর ট্রাকের পর ট্রাক! ট্যুরিজম পয়সা আনে, এজন্য রাস্তার পর রাস্তা তৈরি হচ্ছে, সিঙ্গল লেন ডাবল হচ্ছে বিয়াসের পাশে, সবচেয়ে উঁচু পাহাড়ের মাথায় পৌঁছে যাচ্ছে জেসিপি। ধুলোভরা গাড়ি চলার রাস্তাই হয়ত খুব শিগগিরই উন্নয়নের একমাত্র প্রতীক হয়ে উঠবে।
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাপরিবেশ ভাবনায় ভারতীয় সংস্কৃতি সাহিত্য: সেকাল-একাল - সন্তোষ সেন
০৫ জুন ২০২৪ | ৫০৪ বার পঠিতপরিবেশ বিপর্যয় আজ রাষ্ট্রীয় সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্ব চরাচরে পরিব্যাপ্ত। পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বেড়ে ১.৪৪ ডিগ্রির ঘরে, কোন প্রান্তে তীব্র দাবদাহ- খরা-তাপপ্রবাহ; অন্যত্র প্রবল বৃষ্টি-বন্যা-ধস, এমনকি দুটো বিপরীত এক্সট্রিম আবহাওয়া প্রায় একই সময়ে একই স্থানে আছড়ে পড়ছে। হিমবাহের অতিদ্রুত গলন, জল বাতাস নদীর দূষণ জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে প্রবলভাবে। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে সংবিধান-গণতন্ত্র-পরিবেশের সংকট সব জড়াজড়ি করে জট পাকিয়ে তুলেছে। প্রবল মূল্যবৃদ্ধি, বেকারি, আর্থিক বৈষম্য সহ পরিবেশ সংকটের মূল কারণ দেশি-বিদেশি বহুজাতিক কোম্পানির নির্বিচারে জল জঙ্গল জমি পাহাড় নদী: প্রকৃতির সব উত্তরাধিকার লুটেপুটে ধ্বংস করা।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালশিক্ষা নয়, ভিক্ষা - সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায়
০৫ জুন ২০২৪ | ১৩৫৮ বার পঠিতকাল থেকে দেখি তথাকথিত বাম-সমর্থকরা ভর্তি করে লিখে চলেছেন, "শিক্ষা নয় জিতল ভিক্ষা"। আশ্চর্য হইনি, কারণ সিপিএমের মিছিলে গুচ্ছের লোক হয়, কিন্তু ভোট পায় বিজেপি। এঁদের সঙ্গে বস্তুত শাইনিং চাড্ডিদের বিশেষ তফাত নেই। রাজনীতি-ফিতি কিচ্ছু না, এঁদের মূলত দুটো দাবী। এক, বাম প্রার্থীরা খুব শিক্ষিত। দুই, পশ্চিমবঙ্গে হাইফাই চাকরি নেই, তাই বেঙ্গালুরুতে (কিংবা টিম্বাকটুতে) গিয়ে করেকম্মে খেতে হয়। শিক্ষিতরা খুব উঁচুদরের লোক, বাদবাকি ফালতু, এটা তাঁদের মাথার মধ্যে গেঁথে আছে, আর শিক্ষিতদের চাই মোটা-মাইনের চাকরি, এইটাকে তাঁরা প্রকৃত কর্মসংস্থান ভাবেন। দুটোই খুব সত্যি হতেই পারে (নাও পারে)। কিন্তু সেটা সমস্যা নয়, সমস্যা হল, এই দুটোই, বামপন্থা ছাড়ুন, যেকোনো মধ্যপন্থী জনপ্রিয় রাজনৈতিক চিন্তারই ঠিক উল্টোদিকে। মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্তদের কর্মসংস্থানের জন্য বিশ্বের প্রায় কোনো জনপ্রিয় নীতিই নির্ধারণ হয়না, হলেও মুখে বলা হয়না। খেটে-খাওয়া-মজদুর ইত্যাদিদের কথা অন্তত কাগজে-কলমে লেখা থাকে, কারণ বুক-বাজিয়ে "আমরা এলিট" বলার মতো দুঃসাহস নেহাৎই আত্মহত্যাপ্রবণ না হলে কোনো রাজনৈতিক দলই দেখায়না।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালযে যেখানে দাঁড়িয়ে - প্রবুদ্ধ বাগচী
০৩ জুন ২০২৪ | ২৩২ বার পঠিতl লোকসভা ভোটের সম্ভাব্য ফলের রাজনৈতিক বিশ্লেষণ
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালদোলজ্যোৎস্নায় শুশুনিয়ায় - ১৬ - সমরেশ মুখার্জী
০৩ জুন ২০২৪ | ১১৪ বার পঠিতআশির দশকে যাদবপুরের কয়েকটি ছাত্রছাত্রী শুশুনিয়া পাহাড়ে গেছে শৈলারোহণ অভ্যাস করতে - সেই ভিত্তিতে এই আখ্যান … বেশ লাগছে সুমনের। যেন ডিসেম্বরে বেসিক কোর্সে যা শিখেছে তারই একটা রিফ্রেশার্স কোর্স হচ্ছে
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালবুথফেরত ভূত - সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায়
০২ জুন ২০২৪ | ১৫৪৫ বার পঠিতবুথফেরত সমীক্ষা দেখে আপনি কি ভেঙে পড়েছেন? তাহলে শুনুন, চ্যানেলে চ্যানেল গতকাল যে সব পরিসংখ্যান পেশ করা হয়েছে তার বেশিরভাগ-ই ঢপের চপ। তেলে জল নয়, জলেই দুফোঁটা তেল। একেই পরিশীলিত ইংরিজিতে বলে স্ট্যাটিস্টিকাল মার্ভেল। উদাহরণ? কত চান? ১। রাজস্থান। News24 পূর্বাভাস দিয়েছিল যে রাজস্থানে বিজেপি ৩৩টি আসন জিতবে। জিততেই পারে, অঙ্কের হিসেব যখন। কিন্তু সমস্যা একটাই। রাজস্থানে আছেই মোট ২৫টি আসন। ২। হিমাচল। হিমাচলে Zee News এনডিএকে ৬-৮টি আসন দিয়েছিল। সেটাও অসম্ভব কিছু না, চারদিকে মোদি তরঙ্গ। কিন্তু সেখানেও সমস্যা একটাই। সেখানে আছে মাত্র ৪টি লোকসভা আসন আছে।
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাএক্সিট পোল - রমিত চট্টোপাধ্যায়
০২ জুন ২০২৪ | ৬৯৪ বার পঠিতআসুন দেখে নিই এক্সিট পোলের ভিতরের রহস্য
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজালেজ, বেড়াল, তপস্বী এবং ভণ্ড - বেবী সাউ
০২ জুন ২০২৪ | ৭১৫ বার পঠিত হরিদাস পাল
হরিদাস পালবর্তমানে বাঁচা - সমরেশ মুখার্জী
০২ জুন ২০২৪ | ২৪৪ বার পঠিত৬০২ শব্দের এই খাজা ভাবনাটি লিপিবদ্ধ করেছিলাম ডিজিটাল ডায়েরিতে - চার বছর আগে - ১৮.০২.২১ - মনিপালে থাকতে। আজ ভাটের পাতায় চোখ বুলোতে গিয়ে kk - &/ - dc লিখিত তিনটি মন্তব্যে চোখ পড়লো। তার মধ্যে কেকের মন্তব্যের শেষটা বেশ বিমূর্ত - কিছু অনুক্ত অনুভবের আভাসমাত্র রয়েছে তাতে। ঐ তিনটি ভাট মন্তব্যের অনুরণন হিসেবে হপার পাতায় থাকলো অতীতের ডিজিটাল ডায়েরির পাতাটি
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালআমরা কি মাঙ্গলিক? - Mani Sankar Biswas
০২ জুন ২০২৪ | ১৭৯ বার পঠিতপৃথিবীতে প্রাণ কী মঙ্গল গ্রহ থেকে এসেছে?
- আরও বুলবুলভাজা ... আরও হরিদাস পাল ...
-
গুরুচণ্ডা৯-র গ্রাহক হোন
কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে গুরুচণ্ডা৯-র গ্রাহক হোন। গুরুচণ্ডা৯তে প্রকাশিত লেখাগুলি পেতে চাইলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যুক্ত হোন, অথবা, আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলটির গ্রাহক হোন।
- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই
- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... )
(লিখছেন... )
(লিখছেন... Naresh Jana, দ, Kishore Ghosal)
(লিখছেন... Prativa Sarker, Naresh Jana)
(লিখছেন... )
- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন
(লিখছেন... Kishore Ghosal, হীরেন সিংহরায়)
(লিখছেন... Aditi Dasgupta, SUSANTA GUPTA, Kakali Bandyopadhyay )
(লিখছেন... অসিতবরণ বিশ্বাস , মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দালাল)
(লিখছেন... দ, Nirmalya Nag, :|:)
(লিখছেন... Rouhin Banerjee, পোকো, hmm)
- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... যোষিতা, musil, যোষিতা)
(লিখছেন... অরিন, অরিন, অমিতাভ চক্রবর্ত্তী)
(লিখছেন... সমরেশ মুখার্জী, Kishore Ghosal, syandi)
(লিখছেন... পাপাঙ্গুল, দীপ, দীপ)
(লিখছেন... kk, দীপ, dc)
- কি, কেন, ইত্যাদি
- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...
- আমাদের কথা
- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...
- বুলবুলভাজা
- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...
- হরিদাস পালেরা
- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...
- টইপত্তর
- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...
- ভাটিয়া৯
- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...