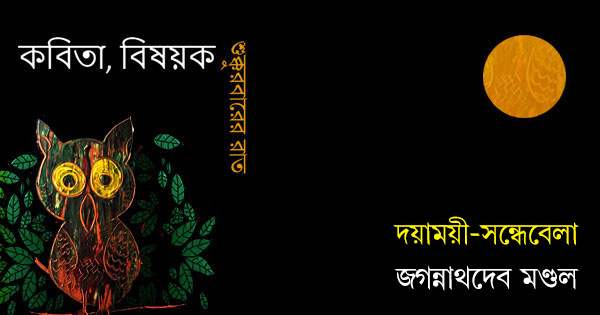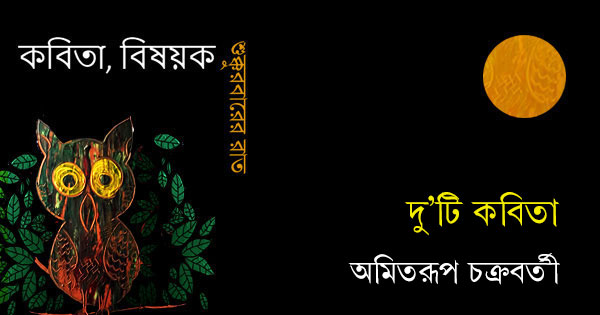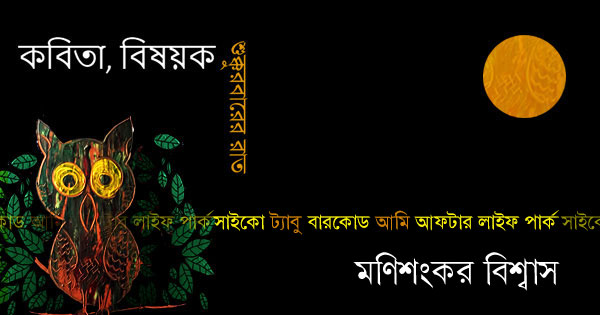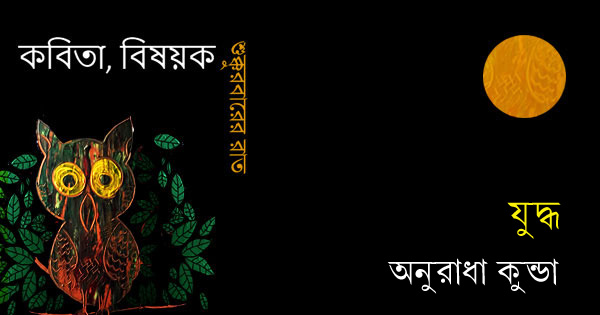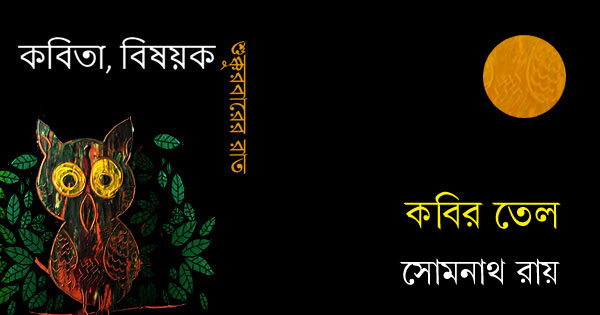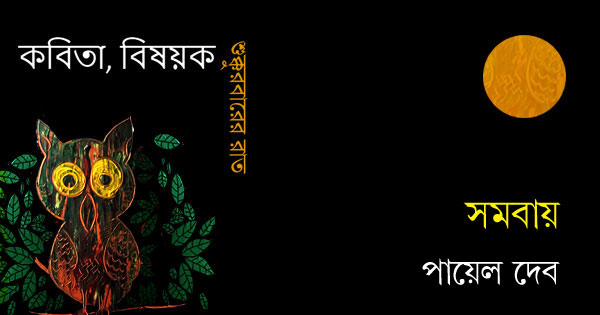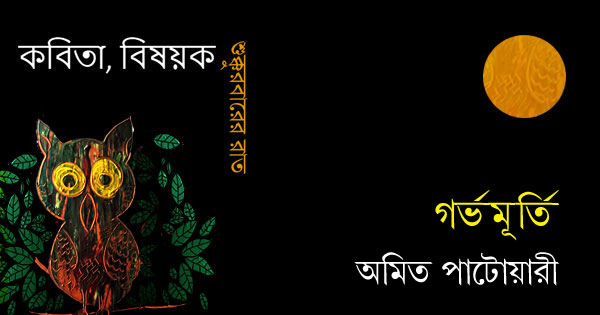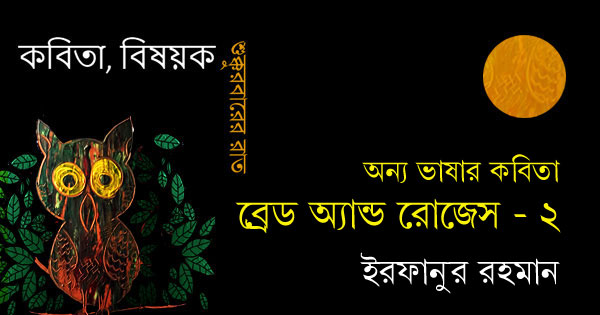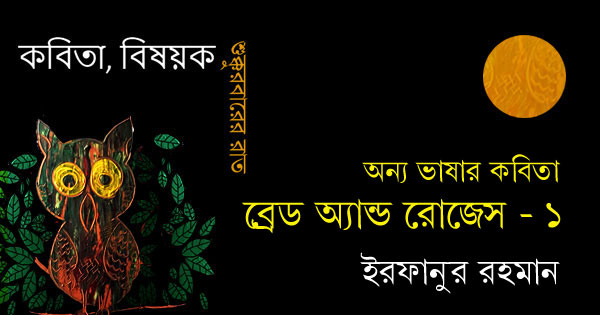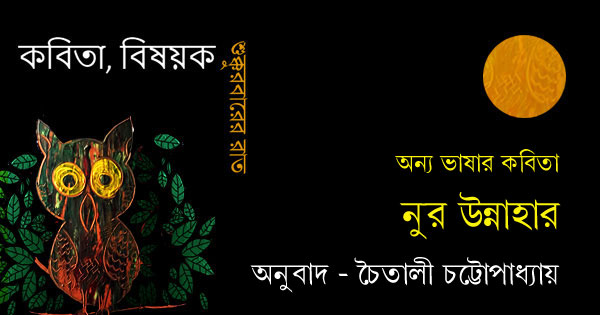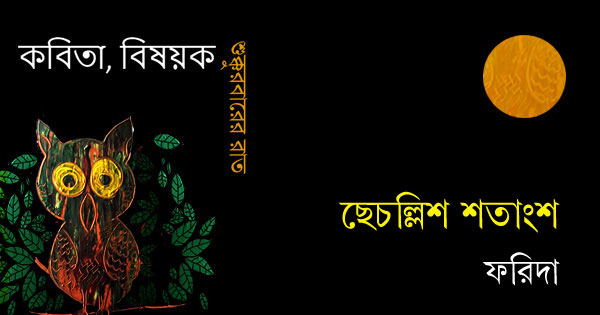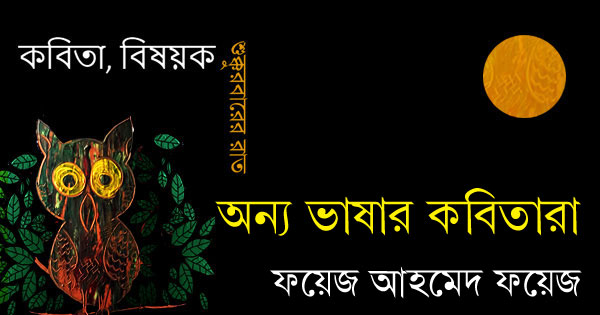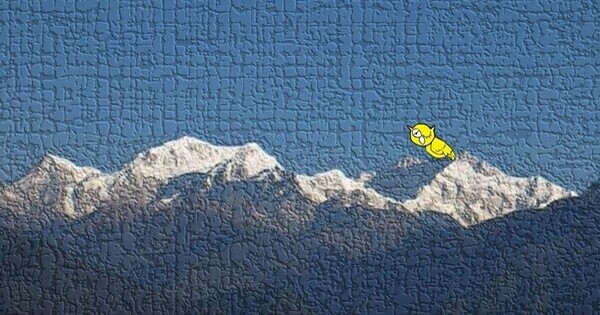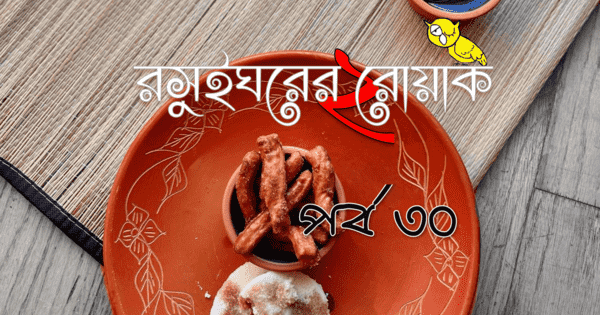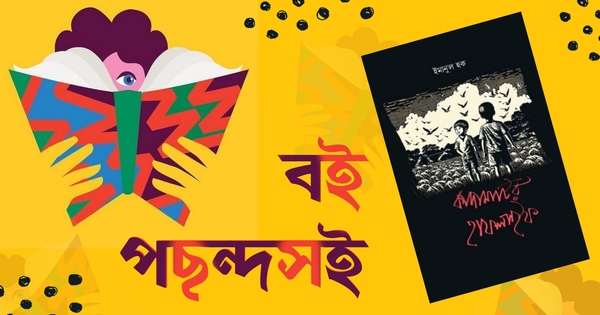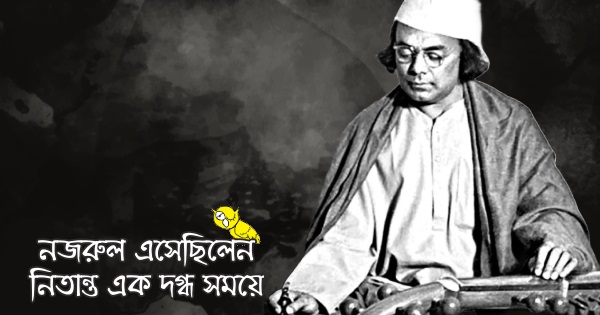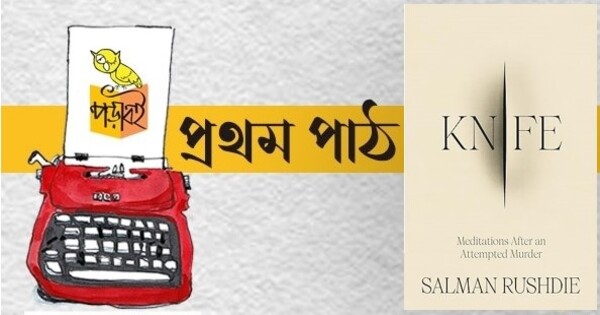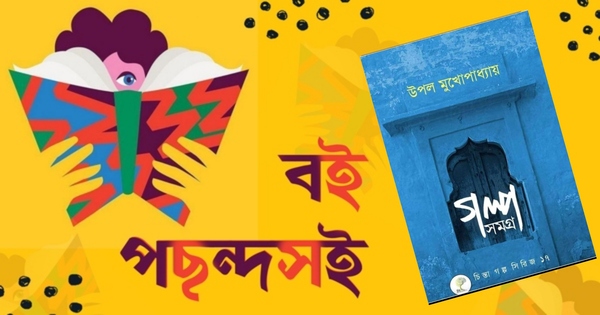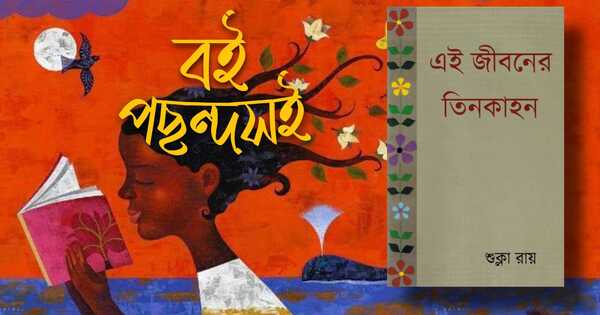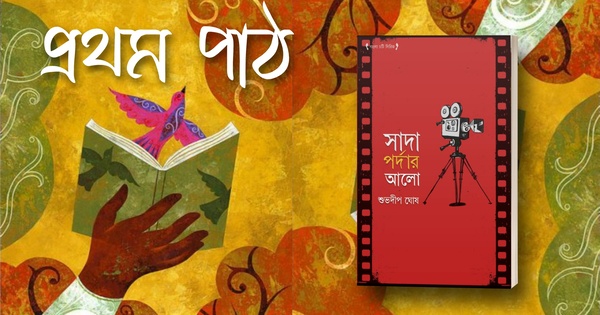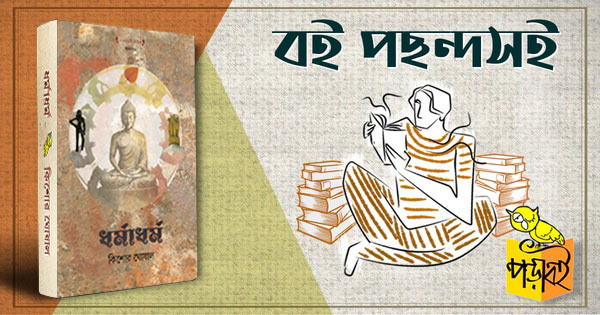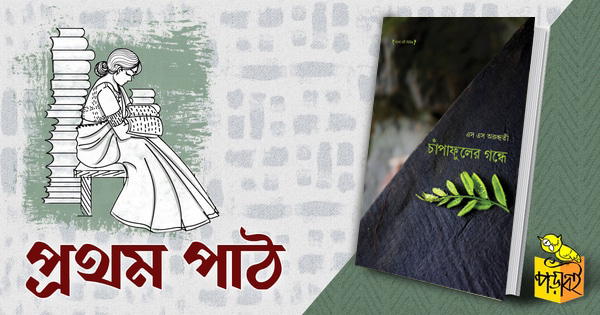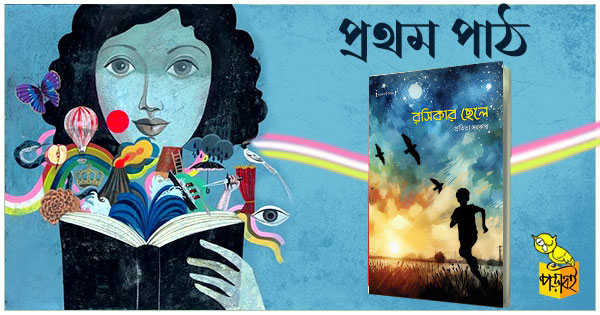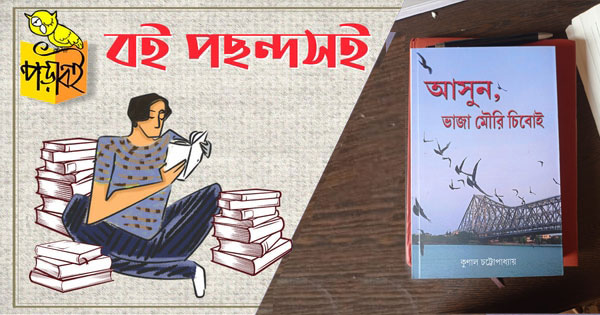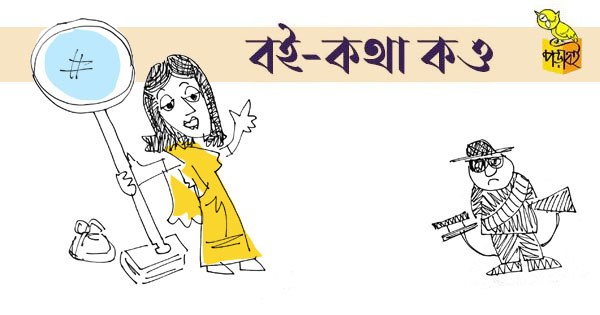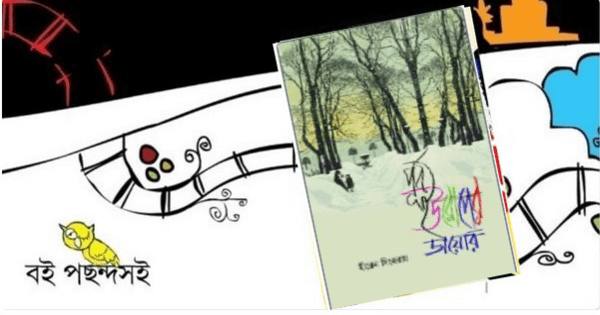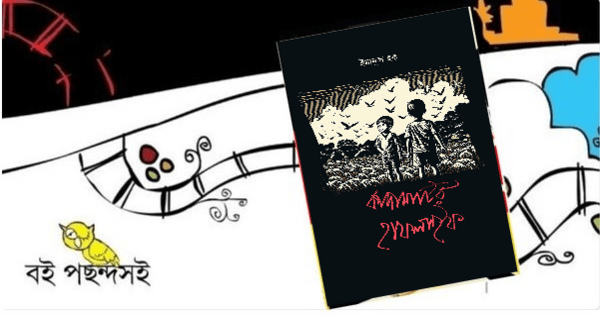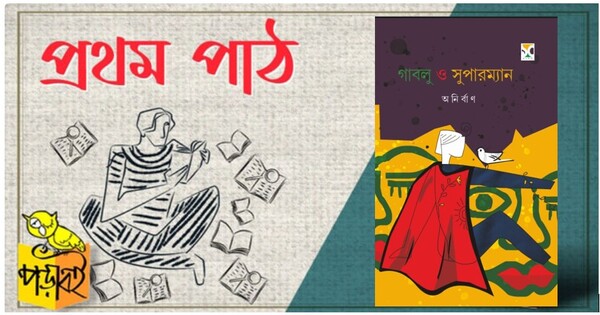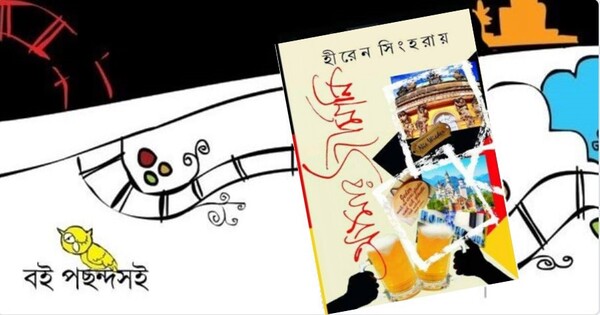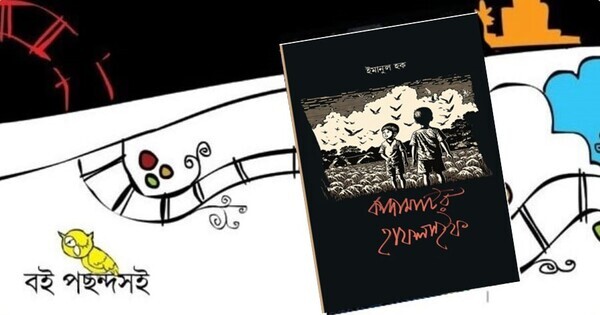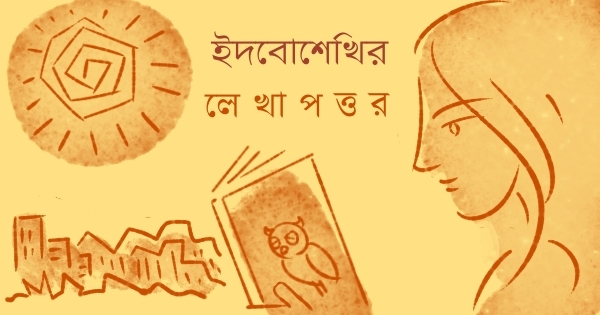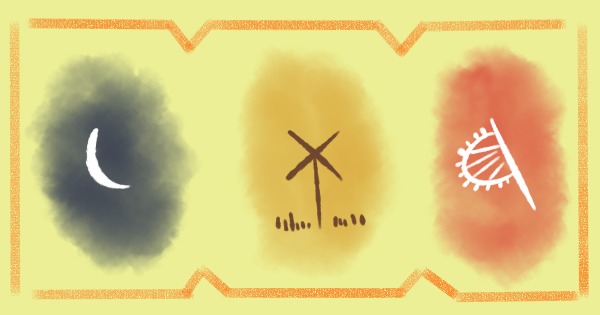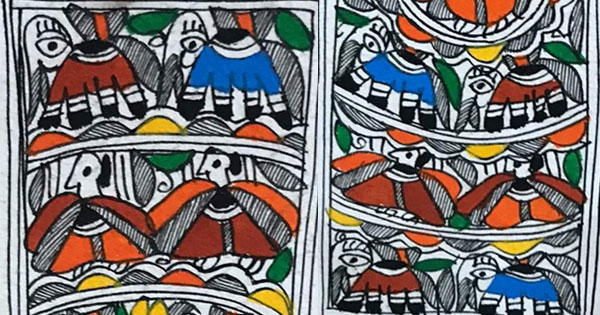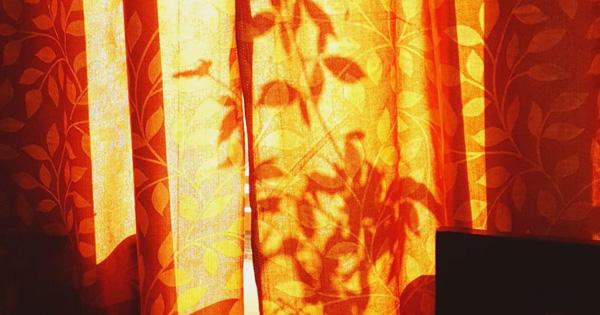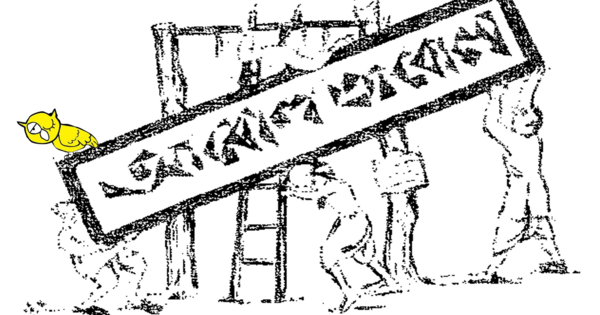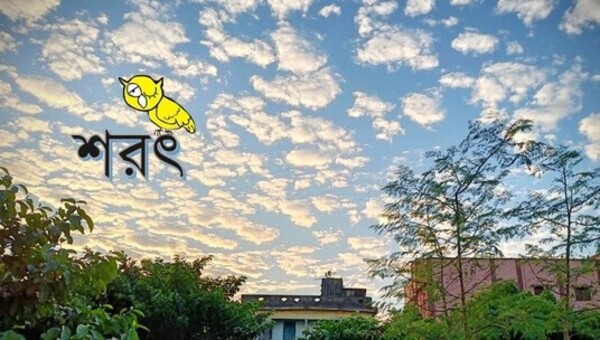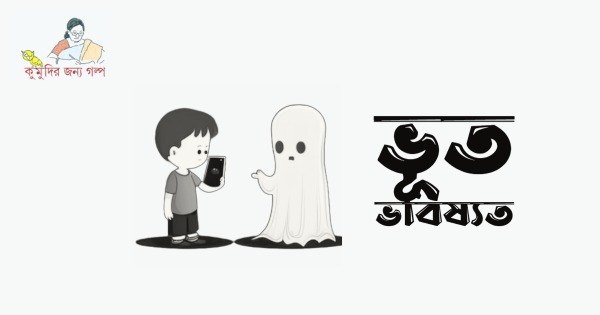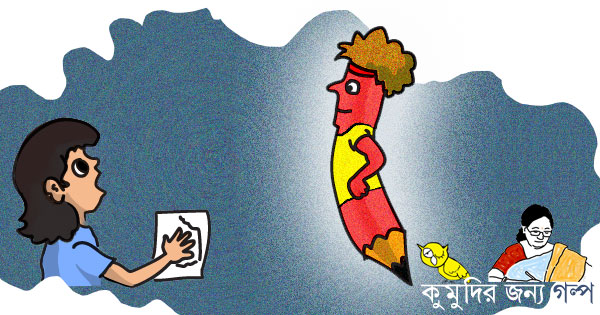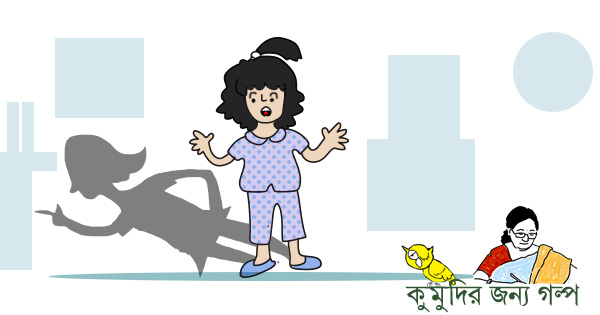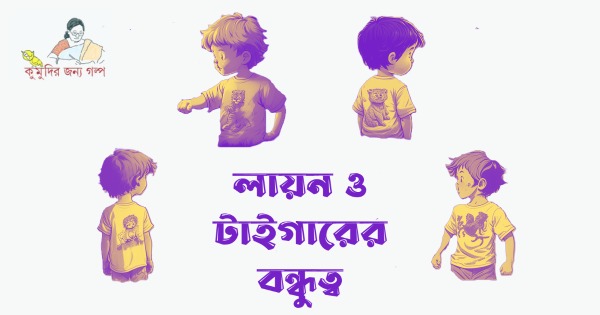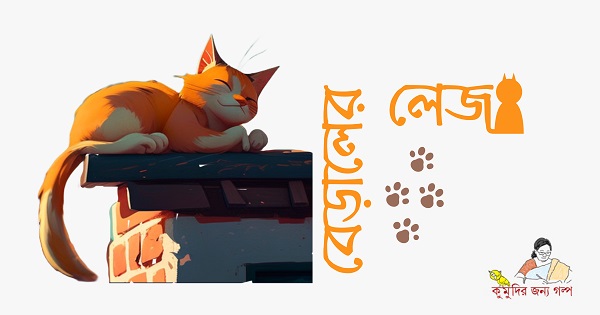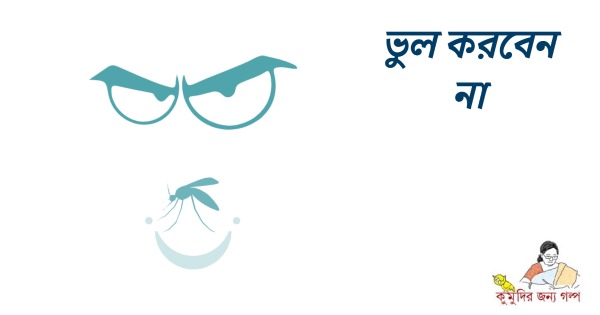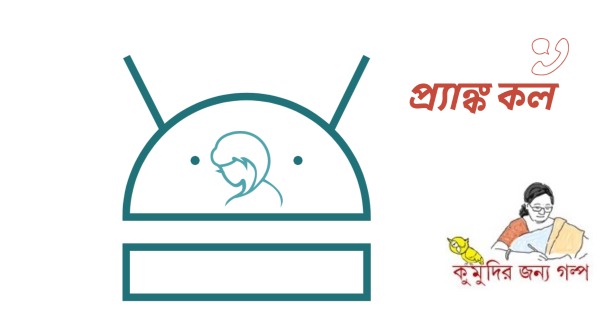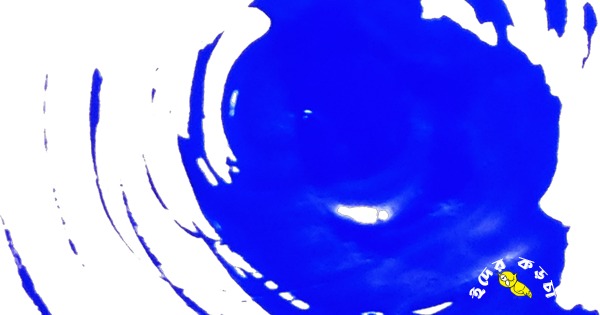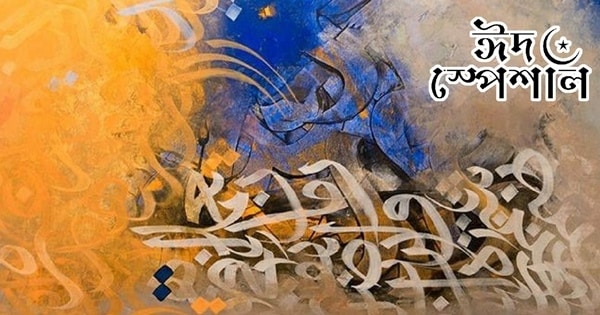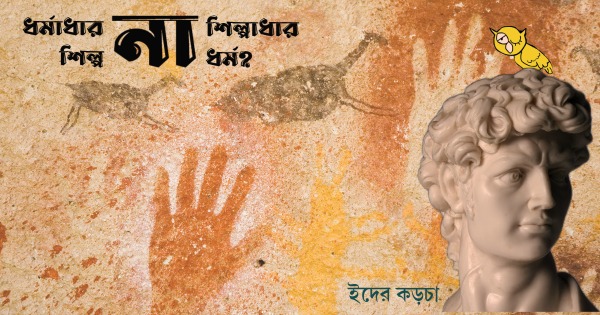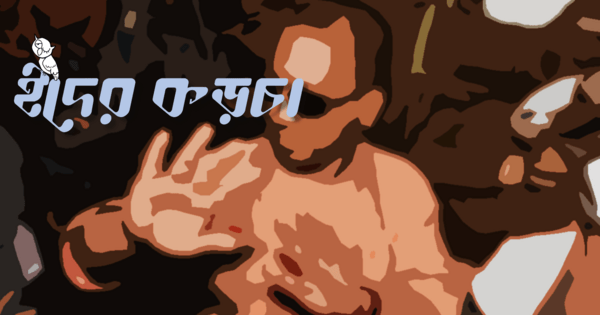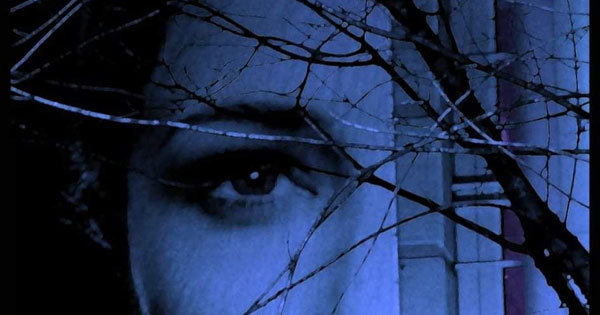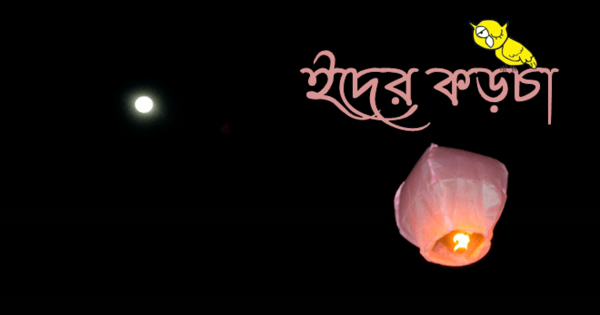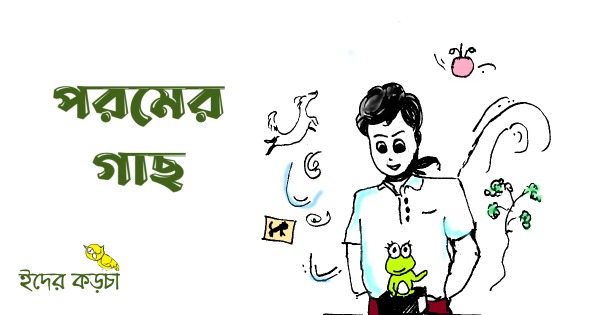তাজা বুলবুলভাজা...
কাদামাটির হাফলাইফ - ইট পাথরের জীবন - ইমানুল হক | ছবিঃ রমিত চট্টোপাধ্যায়কথা - ৩৬আমি একবার ইস্কুলের জানালার বাঁশের কঞ্চির শিক ভেঙে পালিয়ে পুকুরে ঝাঁপ দিয়েছিলাম। গুটিবসন্তের টীকা নেওয়ার ভয়ে। সেটা ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দ। তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ি। ক্যাম্বিসের ব্যাগ নিয়ে একজন স্বাস্থ্যবান মানুষ আসতেন গ্রামে। বিরাট গোঁফ। আজম বলে, ওর মনে হতো, এই আসল যমদূত। আজরাইল। মানুষ সেজে আসতো। তাঁর ব্যাগে টিটেনাসের ইঞ্জেকশন। নিতে হতো। কাটা ছেঁড়া দেখলেই ফুঁড়ে দেন। ইঞ্জেকশন নিয়ে বেদম জ্বর।আর তখন তো রোজ কাটা ছেঁড়া। দুই পায়ের মাঝের আঙুলের নখ তো প্রায় কারুরই থাকতো না। ঘটিং-এ লাগতো। বা শুকনো উঁচু এবড়ো খোবড়ো রাস্তায়। তখন তো পিচের পাকা রাস্তা বা কংক্রিটের হবে গ্রামে কেউ স্বপ্নও দেখেনি। উদাসীন পথ চলি। রাস্তায় কাগজ ঠোঙা পেলে কুড়িয়ে কুড়িয়ে পড়ি। পড়ার তীব্র খিদে। এ বাড়ি সে বাড়ি ঘুরি। বই জোগাড় করি। এতো বই কোথায়? একবার, রায়নার কাছে হামিরপুরে মায়ের খুড়তুতো বোনের বাড়ি গিয়েছিলাম। কতো কতো পুঁথি। সেই প্রথম পুঁথি পড়া। চালের বাতায় গোঁজা ছিল। ডানদিক দিয়ে লেখা।আরবি কায়দায়। পুঁথি পড়ার খুব ইচ্ছে। কেউ সন্ধান দিতে পারেন?তা রাস্তায় কাগজ পড়ার সুবিধার কথা তো বলেছি, আলেকজান্ডারের মায়ের নাম কী? অলিম্পিয়া। এটা জানানোর কথা পাঠকের জানা। সেকালে গল্পের বইকে বলতো, আউট বই। আউট বুক পড়ায় নাম জোটে।লোকে বলতে লাগলো, ব্রেনি ছেলে। সেকালে বুদ্ধিমান নয়, ব্রেনি বলা হতো।তো সেই যমদূত দেখি থ্রিতে টীকা দিয়ে আমাদের দ্বিতীয় শ্রেণিতে ঢুকছে। একটু আগে বাবারে মা রে, মেরে ফেললে রে-- শুনেছি।ইঞ্জেকশনে আজও ভয় করে, আর এ ব্যাটা হাতে ফুটফুট করে একবার নয়, পাঁচ সাতবার ফোটাবে।যমদূতকে দেখেই আমি জানালার বাঁশের কঞ্চির শিক ভেঙে ঝাঁপ দিয়েছি। বাঁকা পুকুর ছিল পাশেই। পুকুরের পাড় গড়ানে হয়। গড়িয়ে গড়িয়ে পুকুরে।কাজী পাড়ার মাস্টারমশাই ছিলেন ছেলেধরার মাস্টার। কেউ স্কুল না এলে তার বাড়িতে চার পাঁচজন ষণ্ডা ছেলে পাঠিয়ে দিতেন।যা ধরে আন।চ্যাংদোলা করে ধরে আনতো সব।তো আমাকেও ধরে নিয়ে যাওয়া হলো পুকুরের জল থেকে।মাথায় গায়ে জলে ভর্তি।ওই অবস্থায় একটু মুছিয়ে দেওয়া হল টীকে।আমরা টীকেই বলতাম।কাজীপাড়ার মাস্টার মশাইয়ের সামনে শম্ভুবাবু বললেন, তুই না চে গুয়েভারা হবি, বিপ্লবীরা কি ভয় পায়?তো, চে গুয়েভারার নামে নিজেকে সাহসী দেখাতে হলো।কিন্তু মনে মনে ভাবলাম, শ্লা, আজরাইল, তোকে ফাঁকায় যদি পাই গুলতি মেরে গোঁফ খুলে নেবো।টীকার জেরে খুব জ্বর এলো।পুকুরের লাফ ঝাঁপ করে টীকার শোক ভোলা গেল।করোনা ভ্যাকসিন টীকার কথা মনে করিয়েছে। পুকুরে একটা জনপ্রিয় খেলা ছিল: ঝালঝাপটা।মানে পুকুরের পাড়ের গাছ থেকে জলে ঝাঁপ দেওয়া। একজন পাহারাদার। ধরবে।সেই খেলা খেললাম সব টীকে ওয়ালারা। জল শান্তি দিল। বাড়িতে বললো, জলের জন্য জ্বর।আমরা বুঝি, টীকের জ্বর।জল জ্বালা ভুলিয়েছে।ঝালঝাপটা খেলায় একজন পাহারাদার। বাকিদের কাজ জলে ঝাঁপ দেওয়া। পাহারাদারের ছোঁয়া এড়িয়ে। তবে সময় সময় পাহারাদার গাছেও উঠতো পারতো। তাঁর সামনে তিনটে পছন্দ।এই ছড়া বলা হতো:ঝাল ঝাপটা, পানের বোঁটারাখাল ছেলে কি লেঙ্গা?সর্ব লিঙ্গা/পানি লিঙ্গা/ গাছ লিঙ্গা?মানে কোথায় কোথায় গিয়ে ছোঁবে খেলিকে?সর্বলিঙ্গা? সব নেবে?জল/ পানি?না গাছ?পাহারাদারের কাজ বলা।এই ঝালঝাপটা খেলতে খেলতে একবার তালপুকুরে পায়ে কাচের ভাঙা বোতল ঢুকে গেল।ইঞ্জেকশনে নেওয়ার ভয়ে কাপড় বেঁধে ছিঁড়ে গেছে বলে চালানো হল।খুব কষ্ট গেল কদিন।পায়ের তলা কাটা অনেকটা।পুনশ্চ: সপ্তম শ্রেণিতে পড়ার সময় আমার বসন্ত হয়। যদিও সেটা গুটি বসন্ত নয়। বসন্তের টীকার দাগ কিন্তু বয়ে বেড়াচ্ছি।প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আরেকটি গল্প খুব মনে পড়ছে। লেখা যাক। বল, কে বিয়ে করবি? যোগ্যতা কী? মাস্টারমশাইয়েরপ্রশ্ন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। ছাত্রদের দুজনকে। স্বাধীন দেশে রাজা এবং প্রজার ধারণা এক মানসিক দাসত্ববৃত্তি থেকে আসে। তাই সাধারণতন্ত্র না বলে প্রজাতন্ত্র দিবস বলেন কেউ কেউ। । আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে খুব ঘটা করে পালন হতো ২৬ জানুয়ারি ও ১৫ আগস্ট। প্রধানশিক্ষক ছিলেন আমার বড়োমামা। কংগ্রেসের বড়ো নেতা। বোঁদে দেওয়া হতো। পতাকা তোলার পর গোটা গ্রাম মিছিল করে ঘোরা শেষে। মাঝপথে কেউ যাতে না পালায়, তাই শেষে মিষ্টি। আমরা সিপিএম বাড়ির ছেলে। পিছনের দিকে থাকতাম। বন্দে বলে আওয়াজ উঠলেই আলতো করে বলে উঠতো কেউ কেউ, বোঁদে ছাগলের পোঁদে।তবে বোঁদে খাওয়ার সময় এ-সব কারও মনে থাকতো না। আমার মনে পড়ে না জুনিয়র হাইস্কুলে এ-সব পতাকা উত্তোলনের রেওয়াজ ছিল কি না! তবে সেহারা স্কুলে পড়ার সময় বেশ ভিড় হতো। ছাদে। বক্তৃতাও হতো। মিল মালিকের ছেলে কংগ্রেসের অবদান বললে, তেড়ে আধঘন্টা বক্তৃতা করে ধুইয়ে দিয়ে বলেছিলাম, ইয়ে আজাদি আধা হ্যায়।টাটা বিড়লা গোয়েঙ্কারা দেশ লুঠছে। তখন তো আদানি আম্বানিদের দেখি নি। তাহলে কী বলতাম জানি না। তখন বলেছিলাম, মাথাপিছু ৬০০ টাকা ঋণ। এখন দেশের ঋণ ধরলে মাথা পিছু দুই লাখ টাকা। কিন্তু কোনও বক্তব্যে সে-সব আসে না। কেন? কে বলবে! আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মান খুব ভালো ছিল। সুনীল হাজরা, শম্ভুনাথ থান্দার, কুর্চিগড়ের মাস্টারমশাই অসাধারণ ছিলেন। খুব অনুপ্রাণিত করতে পারতেন। মাস্টারমশাইদের এক দুজন করে প্রিয়পাত্র থাকতেন। সুনীলবাবুর যেমন সেলিম মামা ও আজম। আমি শম্ভুবাবুর।ছাত্রদের নিয়ে খুব আশাবাদী ছিলেন মাস্টারমশাইরা।কাজীপাড়ার মাস্টারমশাইয়ের কোনো বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিল না। সবার কাছে তিনি বন্ধু। সম্পর্কে দাদু হতেন। ভূগোল পড়াতেন। মজা লাগতো। অস্ট্রেলিয়া ইংল্যান্ড আমেরিকা-- এমন ভাবে হাত দেখিয়ে দেখাতেন, মনে হতো পাশের পাড়া। অ্যাটলাস ছিল একটা বড়ো মাপের। তাতে দেখাতে হতো।ম্যাপ টাঙিয়ে দিতেন। লাঠি দিয়ে নির্দেশ করতে হতো কোথায় কোন সাগর। ভারত মহাসাগর, আরব সাগর, ভূমধ্যসাগর।আমার মনে হয় কাজীপাড়ার মাস্টারমশাই, আজমের মনে আছে সুনীলবাবুকে। আমাদের ক্লাসে একজন সুন্দরী মেয়ে পড়তো। পড়াশোনায় ভালো। বড়োলোকের মেয়ে। তার প্রেমে পড়ে পাগল অনেকেই। আমাদের ভাগ্নি হয়। আমি আজম কাজেই ওই দলে নাই। দুজন প্রকাশ্যেই বলতো। এবং মারামারিও করতো প্রায়ই। এটা কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণির ঘটনা।একদিন খুব মারামারির পর মাস্টারমশাই ক্লাসে এসে বললেন, এর একটা নিষ্পত্তি দরকার। তোরা দুজনে বল, তোরা যে বিয়ে করবি, তোদের যোগ্যতা কী?একজন বলল, আমার বাপের তিনটে বড়ো মড়াই। আরো দুটো ছোটো হয়। এতো বিঘে জমি আছে।দ্বিতীয় জন বলল, আমার দাদো ব্রিটিশ। আমি ওকে ইংল্যান্ড নিয়ে যাবো।ব্রিটিশ মানে তিনি ইংরেজ সেনাবাহিনীতে সৈনিক ছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে লড়েছেন। পেনশন পেতেন। সবুজ রঙের একটা উর্দি পরে ঘুরতেন। ওই এক পোশাক। আর কিছু পরতেন না। মজার মানুষ।তা মেয়েটির মতামত চাওয়া হয় নি।আজকের দিনে এইসব হলে কী যে হতো!(ক্রমশঃ)এই বর্ষার কবিতা - সোমনাথ রায় | ক্লাস শেষ হলে তোমাদের ছাদে কত রঙ প্রথম বর্ষার যত আলোবিকেলের আনত আননমরা রোদে কী মায়া মাখালোমাঠে ছিলো কত খেলাধুলোপ্রবল হুল্লোড় ও হইচইএদিকে সে বৃষ্টি যাকে ছুঁলোতুমি তার ঘুমেতে আসছইযখন ভেঙেছে ঘুম জানোদেখি যে আকাশ-ছোঁয়া বাড়িকাশফুলে উঠোন সাজানোচাঁদোয়া টাঙিয়ে বেলোয়ারিদুপুরের স্বপ্নে মেঘ থেমেতুলি উপচে জল নামে ধারাকখনও তোমাকে পাবো ফ্রেমেথমকে যাবে বৃষ্টিভেজা পাড়াতোমার বাড়ির-ই ছাদ বলেতুমি আসবে তাই তো প্রত্যাশাঋতুর এমন কোলাহলেসেই ভরোসাতে যাওয়া আসাছাদে ছাদে মিটেছে বিকেলে নিদাঘ শীতল করা দিনধারাপাতে সবই মুছে দিলেদিবাস্বপ্ন, প্রয়াসী রঙিনতখনও তোমারই মুখ খুঁজেউঁকি মারছি আকাশের কোণেপা হড়কায় শেওলাসবুজে,আরে! তুমি মেঘের আসনে-ছাদের পাঁচিলে পিড়ি করেগ্যালারির মুখ সারি সারিজানিনা জ্বরের কোন ঘোরেগেছিলাম তোমাদের বাড়ি! বর্ষার পদ সে-কবিতা কেন লিখে যাচ্ছি আজও এতদিন ধরে তাই ভাবিঅনর্থক কেন আহ্বান করছি ধারাপাত শব্দ এযাবৎঅথচ অবাক আমি বুঝিইনি আকাশের দাবি সে-বিকেলেরাস্তার আলস্যে ছাউনির নিচে অপেক্ষা করেছে সাইকেলবৃষ্টি থেমে গেলে বাগান উপচে পথে উঠে আসে কলরবকে কে সঙ্গে ছিল? কোনো জলকণা কোনো গাছ তারা কেউ ছোঁবে?রোদ ঠিকরেছে তক্ষুনি বিকেল অবনত হয় এককোণেপুরোনো পাঁচিলে শ্যাওলার রেখা সেই বাড়িটিই টিউশনিভিজে ওঠা বাড়ি দেওয়ালের ধারে জোনাকির আলো পরিসরসন্ধ্যে ছোঁয়া চাঁদ টান টান হয় ইঁটভেজা গলি পথ ধরে আরেকটুক্ষণ থামে সাইকেল, পিছু ফিরে দেখে, ফের চলেসিক্ত সেই পথে দেখছি অবাক প্রতিবছরের পদাবলী- রথযাত্রা সংসার অরণ্যস্বরূপিণীযুদ্ধে জেতা যাবে না যেহেতুপক্ষজোড়া খাবে রাহু কেতুপুণ্য খাবে রাজার কাহিনিমাটি খাবে চাকার পরিধিআকাশে বিষাদ ঢালা রোদভ্রাতৃহত্যা চড়াবে পারদগতিসূত্রে সেরকমই বিধিভিড় জমে ধর্মতলা মোড়েসারি সারি ঢেকে যাচ্ছে মাথাত্রিপলে আটকে গেছে ছাতাবাস ছুটে যায় আরও জোরেকল নড়ে ঝরে কারখানামন্দিরে মাজারে ধূপকাঠিগুঁজে গুঁজে বৃথা হাঁটাহাঁটিশুধু পাল্টে গিয়েছে ঠিকানারাতে ফিরে অপরের ঘরেটাকার বটুয়া খুলে দেখাপাপের বেতনখানি একাচুকিয়েছ অচেনা নগরেদরবারে অনুরূপ ভিড়আয়নার বহুল প্রসারমুখে মুখে বসানো সবারহাতি ঘোড়া খেলনা মাটিরমেলার প্রাঙ্গনে বাজে গানএত বাজে কান চেপে ধরিচেপে রেখে কান্নার লহরীভেঙেছি খেলনা খানখানশুকনো আকাশে রাখা চোখেকতবার খুঁজে মুখ তারপুন: সে বিবরে বারবারফিরে যাওয়া ঝাঁকবাঁধা ঝোঁকেফের সেখানেই ফিরে আসিএকই চেনা মানুষের ভিড়মাথা মেপে উঠেছে প্রাচীরপশুসঙ্গ মেনে বনবাসীতবু এ ফুলেরই মরসুমস্তব্ধ করে দিয়ে রাজপথবনে ভাসে করুণার স্রোততারপর,- বৃষ্টি নামে ঝুম! পূর্বে আসো মেঘ যক্ষবেদনার বিষাদশিলাভার এখনও বুকে চেপে সে সংবেগঅথচ ভুল গ্রহে ভুল বাতাসে বয়ে পূর্ব উপকূলে এসেছ মেঘআকাশে ঢেকে তারা সকালে মুছে রোদ ভরানো জলে ঐ গভীর চোখএ পথে নদী যত ভুলেছে সংযম তোমার বাসনায় আজ চাতককোথায় রেবানদী পাথুরে পথে চলে খিন্নসলিলিনী শীর্ণকায়এখানে দামোদর দুকূল হিল্লোলে দুকূল ভাসানোর অপেক্ষায়কোথায় চলেছিলে ঊষর হিমানীতে কোন কুবেরপুরী সন্ধানেস্বয়ং লক্ষ্মীর আপন ঝাঁপিখানি উজাড় করা ধান এইখানেসেখানে কাকে পেতে কেবল দয়িতের অদর্শনে এক শ্রান্তপ্রাণএখানে ঘাসে ঘাসে হাওয়ার দোলনাতে ঝুলন মিলনের অধিষ্ঠানএই তো সব ছবি সবুজে মিশে গেছে রঙের অভিলাষ আকিঞ্চনসুভাগা মেঘ তুমি এদেশে এসো এসো আকাশ ভরে দাও বজ্রস্বনএখানে মাটি দেশে শ্যামল সমারোহে শ্যামের বাঁশি আর সে রাঙা পদতাকিয়ে নিচে দেখ কত নিবিড় আভা নদীর তীরে ঘাসে কী সম্পদতোমার অবকাশে পাতায় পড়ে রোদ সোনার জলে মোড়ে সবুজ রঙগাছের চূড়াখানি মেঘের ধোঁয়া মাখে তমালশীর্ষটি শ্বেতবরণনারিকেলের পাতা বাজালো ঝমঝম যখন পেলো তালে ঝড়ের দিকবৃষ্টি থেমে গেলে শেওলাকুচি থেকে কার্নিশের গায়ে তার স্ফটিকআমের ডালে ডালে পাতার আবডালে বাসনা জমে ওঠে বর্ণচোরজামগাছের নিচে কালোসবুজে পাতা আষাঢ়সন্ধ্যার আলসঘোরকী পেতে নগরীর পিপাসী গৃহে গৃহে সাজানো দীপমালা চকমিলানএখানে বকুলের আলোআঁধারি মাখা পাতায় মিশে থাকে ঘুমের ঘ্রাণ দেখেছ মায়া লাগে কদমতরু শাখে সবুজ ফুল জাগে প্রতীক্ষায়আওয়ে ভাদর মাহ রাধিকাপ্রণয়ীর প্রণয়ে রেণু যদি পরাগ পায়এখানে প্রেমিকের নিবিড় বাহুভরে সন্তানের মুখে দুধের ভাতএখানে শ্রমে ভিজে পুরোনো সোঁদাঘরে মায়ের আঁচলেতে মুছছে হাতএখানে রূপকথা দিঘিতে ঘাই মারে পিতামহীর দেওয়া মাছের নথপুকুরপাড়ে পথ সবুজ মাটিরঙে কচুপাতায় রোদ দণ্ডবৎদেখোনি প্রান্তরে লালমাটির ঢেউ ঘাসেতে মিশে গেছে ফুলবাসরদেখোনি মহানিম ডালেতে সাজিয়েছে ঘাসের মত উড়ো পাতার ঘরদেখোনি ডুমুরের ছাতায় নামে রাত দেখোনি দুপুরের সে নিশিসুখকলার বেষ্টনী ঘোমটা নিচু করে ভেজা মাটির বুকে রাখছে মুখকাঁঠালবিচি থেকে সবুজ কচি হাত শূন্যে মুঠি খুলে দরদিয়াঅপার রহমতে সমাধি ঘুমে আছে হাজার উপাসক আউলিয়া মেঘনা ভাগীরথী পলিমাটিতে মেশে যেমন আজানেতে মিশছে শাঁখমাঠে ও জলতলে যেমন মিশে আছে লক্ষ কৃষকের হুলের ডাকরুক্ষ ঐ দেশ ভুলেই যেও সেই বিগতজন্মের বিষাদরাতআজ ঝড়ের মুখে পূর্ব অভিমুখে এসেছ এইখানে অকস্মাৎএদেশে এসে গেলে মিশেই যেতে হবে এই মাটিতে জলে নিরুদ্বেগতুমি সবুজ হও আমার বাংলায় বৃষ্টি হয়ে যাও কাজলমেঘবৈদিক গণিত বিপন্ন? - সুনন্দ পাত্র | ছবি : রমিতগত ১২ই জুলাই, শুক্রবার, অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে পনেরোতম আন্তর্জাতিক গণিত-শিক্ষণ কংগ্রেস (International Congress of Mathematics Education; ICME)-এর সম্মেলন থেকে অধ্যাপক জয়শ্রী সুব্রহ্মনিয়নকে (SRM University, Andhrapradesh) নিরাপত্তা-আধিকারিকরা প্রহরা দিয়ে বের করে দেন। তাঁর ব্যাজ বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং রেজিস্ট্রেশন প্রত্যাহার করা হয়। কারণ হিসেবে তাঁকে বলা হয়, যে, সেদিন সকাল ন-টায় অধ্যাপক আশিস অরোরা-র ‘Reviving Ancient Wisdom: Vedic Mathematics for Modern Learning’ শীর্ষক অধিবেশনে তাঁর করা কিছু মন্তব্যকে কিছু অন্য অংশগ্রহণকারীর শাসানিমূলক ও ভীতিপ্রদ মনে হয়েছে। যদিও পরেরদিনের একটি প্যানেলে অংশগ্রহণ করার জন্যে তাঁকে একটি সাময়িক ব্যাজ দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু অধিবেশন-অন্তে আবার তাঁকে প্রহরা দিয়ে বের করে দেওয়া হয়। কতটা আতঙ্কের উদ্রেককারিণী এই ভারতীয় গণিত-অধ্যাপক? কতটা ভয়ঙ্কর তাঁর উপস্থিতি, যার ফলে তাঁকে শিক্ষকদের সম্মেলন থেকে বের করে দিতে হয়? ‘বৈদিক গণিত’ ঠিক কীরকম বিপন্ন হয়েছিল তাঁর উপস্থিতিতে? এসব কথা জানতে, সেই অধিবেশনেরই আরেক শ্রোতা এবং ওই সম্মেলনের আরেক নিমন্ত্রিত বক্তা, ওহায়ো স্টেট ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক থিওডর চাও (Theodore Chao)-এর বয়ান পড়ে ফেলুন। মূল লেখাটি ইংরেজিতে, পাবেন এখানে। লেখাটি অধ্যাপকের অনুমতিক্রমে বাংলায় অনুবাদ করে দেওয়া হল —“আমার নাম ‘থিওডর চাও’; ওহায়ো স্টেট ইউনিভার্সিটির অঙ্কের অধ্যাপক। ২০২৪-এ অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে হওয়া ICME সম্মেলন আমায় এ বছরে একজন বক্তা হিসেবে আমন্ত্রণ করে সম্মানিত করেছে। এ আমার দ্বিতীয় ICME সম্মেলনে আসা, দুনিয়া জুড়ে অঙ্ক শেখানোর নানা দিক নিয়ে শুনতে, আলোচনা করতে ভালোবাসি বলে আর অতীতের অবিচার কীভাবে নির্মূল করা যায় শিখতে চাই বলেই অংশগ্রহণ করেছি। গতকাল—১২ই জুলাই, সকাল ন-টায় ‘Reviving Ancient Wisdom: Vedic Mathematics for Modern Learning’ (প্রাচীন জ্ঞানের পুনরুজ্জীবন: আধুনিক শিক্ষায় বৈদিক গণিত) নামের একটি অধিবেশন ছিল, আই কে গুজরাল পাঞ্জাব প্রায়োগিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আশিস অরোরা যার বক্তা ছিলেন।অঙ্ক আর অঙ্ক কষতে শেখানো পদ্ধতিগুলোর সঙ্গে সংস্কৃতির যোগাযোগ—বিশেষ করে ইউরোপের বাইরে যা হয়—তা নিয়ে আমার উৎসাহ আছে বলেই এই অধিবেশনে অংশগ্রহণ করা। ভারতের অঙ্কের ইতিহাস নিয়ে আমার বোধ সীমিত হওয়ায় এই অধিবেশন নিয়ে আমার বেশ কৌতূহল ছিল আর আমি খোলা মনেই এতে অংশগ্রহণ করি, বৈদিক গণিত বলে যা দেখানো হবে, তার সঙ্গে অবিচার আর নিপীড়নের সমস্যা জড়িয়ে থাকবে – এমন কোনো অনুমান ছাড়াই। ব্যক্তিগতভাবে, অধিবেশনটি আমায় হতাশ করেছে—যদিও জঘন্য মনে হয়নি। বৈদিক গণিতের উৎপত্তি আর ভারতে যাঁদের বৈদিক গণিতজ্ঞ বলে ভাবা হয়, তাঁদের নিয়ে অধ্যাপক অরোরা খুব সামান্যই বললেন। যেহেতু এই অধিবেশনটি আসলে এক কর্মশালা (workshop) হওয়ার কথা, তাই অঙ্কের সাংস্কৃতিক ইতিহাস নিয়ে উনি আরো কিছু বললে, বা আমাদের সেই আলোচনায় জড়ালে আমার মনে হয় ভালো হত। তার বদলে এই ইতিহাস অংশটুকু উনি দ্রুত, পনেরো-কুড়ি মিনিটে বুড়ি ছুঁয়ে গেলেন। এরপর অধ্যাপক অরোরা নানা গাণিতিক পদ্ধতি উপস্থাপন করে তাদের বৈদিক গণিতের বিশেষ রূপ হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করলেন। এই পদ্ধতিগুলিকে নিয়ে কাটাছেঁড়া, খেলাধুলো করার বা তাদের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করা সুযোগ পেলে তা আমার খুবই চিত্তাকর্ষক মনে হত—সন্দেহ নেই। বদলে, অধ্যাপক অরোরা সোজা উদাহরণে চলে গেলেন, আর আলাদা আলাদাভাবে, অঙ্কের জাগতিক দুনিয়ার বাইরে কী করে এদের নির্দিষ্ট ব্যবহার করা যায়, তার বিস্তারিত বর্ণনা শুরু করলেন। নানা অ্যালগরিদমের মধ্যে বিভিন্ন নির্দিষ্ট মান ব্যবহার করলে তার থেকে ‘গুণ’ (multiplication) পাওয়া যেতে পারে – তার নানারকম পদ্ধতি অবধি আমি তাঁর বক্তব্য অনুসরণ করার চেষ্টা করেছিলাম। এইসব উদাহরণ আমার নিজের বেশ ক্লান্তিকর লাগছিল, কারণ উনি আসলে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন আর শ্রোতাদের সঙ্গে আলোচনায় না গিয়ে উদাহরণ থেকে উদাহরণে হেঁটে বেড়াচ্ছিলেন। মাঝে একবার তো আমি বক্তৃতার মধ্যে মাথা গলিয়ে, যে সাদা বোর্ডটা উনি ব্যবহার করছিলেন, সেটাকে আরেকটু আলোকোজ্জ্বল জায়গায় আনার ব্যবস্থা করলাম, যাতে তা ঘরের অন্যান্য অংশ থেকে আরেকটু ভালো করে দেখা যায়, দর্শকমণ্ডলীকে আরেকটু উৎসাহিত করা যায়। আমি বেশ হতাশ হয়েছিলাম, কারণ এই বক্তৃতাটি কোনো কলেজের অঙ্কের সনাতনী ক্লাসের মতো (ভালো অর্থে নয়) শোনাচ্ছিল, যেখানে বক্তা, শ্রোতাদের সঙ্গে সংযোগস্থাপনের, বা নিদেন তাদের কী মনে হচ্ছে – তা শোনার ন্যূনতম চেষ্টাটুকুও করেন না।এই কর্মশালার এই ব্যাপারটি আমায় হতাশ করেছিল। আমার মতে, ICME-র সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য হল – সকলে মিলে গণিত-শিক্ষণ নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা-অন্বেষণ করা। অতএব, এই সম্মেলনে প্রদর্শিত যেকোনো বিষয়ের এক আবশ্যিক অংশ হওয়া উচিত – অঙ্ক শেখানোর কলাকৌশল আর মানবজীবনের সঙ্গে অঙ্কের যোগ নিয়ে আলোচনার সুযোগ।বক্তৃতা চলাকালীন যে অঙ্ক দেখানো হচ্ছিল, তা অনুসরণ করতে আমাদের—আমি ও আমার পাশে বসে থাকা একজন মহিলার—বেশ অসুবিধে হচ্ছিল। উপস্থাপনাটি যে গতিতে এগোচ্ছিল, তা আমাদের বেশ হতাশ করে। যা দেখানো হচ্ছিল, তা আমাদের কষা উত্তরের সঙ্গে মিলছিল না বলে আমরা আলোচনা করছিলাম—স্লাইডে মুদ্রণপ্রমাদ নেই তো? অধ্যাপক অরোরা এসব মানতে বা আমাদের ধারণা নিয়ে দর্শকমণ্ডলীর সঙ্গে আলোচনা করতে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন না। এই অবস্থায়, বোঝার, শিক্ষার সুবিধের জন্যেই একটু থামা দরকার ছিল বলে আমার মনে হয়েছে।অধিবেশনের প্রায় ৪৫ মিনিট অতিক্রান্ত হওয়ার পর শুনতে পেলাম, ঘরের একজন শ্রোতা প্রশ্ন করেছেন, যে আলোচনার কোনো সুযোগ আছে কিনা। বক্তা বললেন, সুযোগ পাওয়া যাবে, বলে বক্তৃতা চালিয়ে গেলেন। খেয়াল করলাম, আমি আর আমার চারপাশের শ্রোতৃমণ্ডলী সামান্য আশাহত হয়েছি, ওইসময় আলোচনা শুরু না হওয়ায়।সোয়া দশটা নাগাদ, যখন এই দেড় ঘণ্টার অধিবেশনের আর পনেরো মিনিট বাকি, অধ্যাপক অরোরা আলোচনার সুযোগ দিলেন। ততক্ষণে, বোর্ডে যা আঁক কষা চলছিল তা বোঝার আশা আমি জলাঞ্জলি দিয়েছি। অধ্যাপক জয়শ্রী সুব্রহ্মনিয়ন, যিনি আমার এক সারি পিছনে বসেছিলেন, হাত তুললেন।অধ্যাপক সুব্রহ্মনিয়ন দাঁড়ালেন, আর কয়েকটি গোছানো পয়েন্ট তুলে ধরলেন।প্রথমত, অধ্যাপক সুব্রহ্মনিয়ন বললেন, যে, বক্তা দেখানোর চেষ্টা করছেন দুটিমাত্র গণিতের ঘরানা বিদ্যমান, যার একটি ভারতীয়, অন্যটি ইউরোপীয়। তিনি প্রশ্ন করলেন – অধ্যাপক অরোরা অন্যান্য ঘরানা, যেমন চৈনিক, মিশরীয় বা ইনকা গণিত-এর অস্তিত্ব কেন অস্বীকার করছেন, আর এও উল্লেখ করলেন যে এই দৃষ্টিকোণ সমস্যাজনক।দ্বিতীয়ত, অধ্যাপক সুব্রহ্মনিয়ন প্রশ্ন করলেন – বৈদিক গণিতের ধারণাটি যে আসলে ভারতে এখনো বহুল প্রচলিত অন্যায় বর্ণাশ্রমকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে, এই কথাটি অধ্যাপক অরোরা কেন এড়িয়ে গেলেন? ব্যক্তিগতভাবে আমার এই পশ্চাৎপট সম্পর্কে বিশেষ জানা ছিল না, তাই আমি বিষয়টি তুলে ধরার জন্যে অধ্যাপক সুব্রহ্মনিয়নের তারিফ করলাম। আমার মনে হয়, ICME-র মতো সম্মেলনে আমাদের আরো বেশি করে মানবজীবন আর অবিচার—বিশেষ করে অঙ্কের শিক্ষণে অবিচার—নিয়ে আলোচনা করা উচিত। এই তথ্যটির ফলে তাই, যাকে বৈদিক গণিত বলে দাগানো হয় – তার সাংস্কৃতিক ভূমিকা আর পরিবেশ বুঝতে আমার সুবিধে হল।তৃতীয়ত, অধ্যাপক সুব্রহ্মনিয়ন উল্লেখ করলেন, অধিবেশনের গৌরচন্দ্রিকায় বৈদিক গণিতের সূত্র হিসেবে যে সব বই ও প্রবন্ধের উল্লেখ করা হয়েছে, তার কয়েকটি ইতোমধ্যেই তার গৌরব হারিয়েছে। তিনি এমনকি এও উল্লেখ করলেন, যে, সূত্রে উল্লিখিত একজন লেখক তো ‘বৈদিক গণিত’ বলে কিছুর অস্তিত্বই অস্বীকার করেছেন। এই খবরটি আমার পছন্দ হল, কারণ এর থেকে আমার কাছে পরিষ্কার হল, যে, প্রোপাগান্ডা আর সংশোধনবাদী ইতিহাসের অস্তিত্ব শুধু আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের গণিতের প্রেক্ষিতেই গুরুত্বপূর্ণ – তা নয়, এর অস্তিত্ব সর্বব্যাপী। ভারতে গণিতের ভূমিকা নিয়ে আলোচনায় যে বিতর্কের অস্তিত্ব আছে, তা জানতে পেরেও আমার ভালো লাগলো। সবচেয়ে বেশি তারিফ করলাম অন্যায্য বর্ণাশ্রমের সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারটা – ব্রাহ্মণ্যবাদী আদর্শ যে নিজেকে এক এবং অদ্বিতীয় বর্ণ বলে উপস্থাপিত করে, আর ফলত নিজেকে গাণিতিক জ্ঞানের একমাত্র ধারক ও বাহক বলে মনে করে – এ সম্পর্কে আমার অজ্ঞানতার পরিধি নিয়ে আমার ধারণা আরো বলবৎ হল। আমার মতে, এই মন্তব্যগুলি আলোচনা শুরু করার পক্ষে দারুণ ভালো জায়গা। অধ্যাপক সুব্রহ্মনিয়ন যথেষ্ট উচ্চস্বরে কথা বলছিলেন, যাতে ঘরের সকলে তাঁর কথা শুনতে পান, তাঁর কথা আবেগজড়িতও ছিল। তাঁর মন্তব্যগুলি শ্রদ্ধাশীল আর বৌদ্ধিক আলাপচারিতা শুরু করার পক্ষে আদর্শ ছিল। এরপর আরেকজন শ্রোতা উঠে দাঁড়ালেন। তিনি বললেন, যে, বৈদিক গণিতের সমালোচনার জায়গা অবশ্যই আছে, তবে এই অধিবেশনের পক্ষে তা হয়তো যথাযথ নয়। এরপর, সাড়ে দশটা বেজে গেছিল বলেই, অধিবেশন সমাপ্ত হল আর আমরা বাইরে বেরিয়ে এলাম।অধিবেশন শেষ হওয়ার পর আমি অধ্যাপক সুব্রহ্মনিয়নের সঙ্গে দেখা করে তাঁর মন্তব্যের জন্যে ধন্যবাদ জানালাম। তাঁর মন্তব্যগুলি ছাড়া আমি হয়তো খুবই হতাশ হতাম এই অধিবেশন নিয়ে, কারণ গণিত-শিক্ষণ কর্মশালার বদলে এটি যেন বড় বেশি গণিতের ক্লাস বলে মনে হয়েছিল। বৈদিক গণিতজ্ঞ, বৈদিক গণিতের সঙ্গে বাস্তব জীবনের অঙ্কের সম্পর্ক অথবা অঙ্ক শেখানো বা শিক্ষক-শিক্ষণের সঙ্গে তার সম্পর্ক – এই সমস্ত বিষয়গুলি অধিবেশনে বড় তাড়াহুড়ো করে বুড়িছোঁয়া করা হয়েছিল বলে আমার ধারণা। তাঁর মন্তব্যগুলি না করা হলে আমার মনে হত দেড়ঘণ্টার এক আপাত-কর্মশালা থেকে আমি কিছু না শিখেই বেরিয়ে এসেছি। গণিত-শিক্ষণের সঙ্গে আলোচিত বিষয়গুলির যোগ তৈরি করতে আর বৈদিক গণিতের সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বুঝতে অধ্যাপক সুব্রহ্মনিয়নের মন্তব্যগুলি আমায় সাহায্য করেছিল। এই মন্তব্যগুলি থেকে আমি বুঝেছিলাম, যে ‘বৈদিক’ শব্দটি সমস্যাজনক, আর এইভাবে গণিত নিয়ে ভাবার সঙ্গে ক্ষমতা, বর্ণাশ্রম আর সামাজিক অনুক্রম জড়িয়ে রয়েছে। এই লেন্স দিয়ে দেখার ফলে বিশ্বজুড়ে গণিত শিক্ষণের প্রেক্ষাপটে আমি অধিবেশনটিকে দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম।অধ্যাপক সুব্রহ্মনিয়নের মন্তব্যগুলিকে আমার কোনোভাবেই দ্বন্দ্বমূলক বা বৈরীভাবাপন্ন মনে হয়নি। এর ফলে ঘরে কোনোভাবে হিংসা বা হুমকির আবহ তৈরি হয়েছিল বলেও আমার মনে হয়নি। বরং, তাঁর মন্তব্যের ফলেই আলোচনাটি আরো বিষয়ানুগ হয়েছিল। এর পরে আমি জানতে পারি, যে এই অধিবেশনে করা মন্তব্যের ফলে অধ্যাপক সুব্রহ্মনিয়নকে ICME সম্মেলন থেকে বহিষ্কৃত করা হয়। এই সিদ্ধান্ত আমার মতে অন্যায় এবং অন্যায্যরকম কঠোর। ICME-র যা লক্ষ্য, অধ্যাপকের মন্তব্যগুলি অধিবেশনটিকে সেইদিকেই নিয়ে যায়। তাঁর মন্তব্য ছাড়া এটি নিতান্তই ICME-র অনুপযুক্ত, অসংযুক্ত একটি অঙ্কের ক্লাস মাত্র।যদিও আমি ICME গোষ্ঠীর একজন সদস্য এবং একজন নিমন্ত্রিত বক্তা, শনিবারের পরবর্তী যে অধিবেশনগুলিতে আমার অংশগ্রহণ করা ইচ্ছে ছিল, সেগুলিতে আমি আর যেতে পারিনি – অধ্যাপক সুব্রহ্মনিয়নের সঙ্গে ঘটা এই অবিচারের খবর জানতে পেরে।আমার মনে হয়, এই অধিবেশনে আলোচিত বক্তব্যের সঙ্গে ভারতের বর্ণাশ্রমের সম্পর্ক আর অবিচারের ইতিহাস নিয়ে গলা তুলেছেন বলেই অধ্যাপক সুব্রহ্মনিয়নকে অন্যায়ভাবে নিশানা করা হচ্ছে। এও বলে রাখি, উনি একজন ভারতীয় নারী, যাঁর স্বর দৃঢ় আর পাণ্ডিত্যপূর্ণ। তাঁকে আতঙ্কের আসনে বসানোটা বিশ্বজুড়ে চলা নারীবিদ্বেষ আর রেসিজ়মের নকশায় ঠিকঠাক খাপ খায়। অধ্যাপক সুব্রহ্মনিয়নের প্রতি এই আচরণ অনৈতিক, নিরর্থক। এই অভিজ্ঞতার ফলে ICME সম্মেলনের আয়োজকদের বিচারবোধের প্রতি আমার মনে সন্দেহ জন্মেছে, এমনকি অন্য গাত্রবর্ণের নারীদের পক্ষে এই সম্মেলন নিরাপদ কিনা, তা নিয়েও প্রশ্ন জেগেছে। ভবিষ্যতের ICME কি তবে গনিতশিক্ষায় শ্বেত-প্রভুত্ব, নারীবিদ্বেষ আর বনেদিপনার এক আখড়া হয়ে উঠবে? আমি কোনোভাবে সেই ICME-র অংশ হতে চাই না।”অধ্যাপক জয়শ্রী সুব্রহ্মনিয়নের সঙ্গে হওয়া এই অন্যায়ের প্রতিবাদে একটি স্বাক্ষর-সংগ্রহ অভিযান শুরু হয়েছে কয়েকদিন আগে। প্রয়োজন মনে করলে তাতে নাম দিয়ে সই করে আসুন। আশা করি, এই নিয়ে আরো লেখালেখি হবে। তবে সম্ভাবনা খুব কম, কারণ বৈদিক গণিত নিয়ে গুচ্ছ গুচ্ছ লেখা ঝটিতি পাওয়া সম্ভব হলেও, মিনিট দশেকের গুগল সার্চে এই ঘটনার কোনো উল্লেখ মিডিয়ার কোত্থাও চোখে পড়লো না।“And I tell you, call me daft, but the words of the prophecies are changing. The alterations are slight. Clever, even. A word here, a slight twist there. But the words on the pages are different from the ones in my memory… I sense a craftiness behind these changes, a manipulation subtle and brilliant… I have come to only one conclusion. Something has taken control of our religion, something nefarious, something that cannot be trusted. It misleads, and it shadows.”— The Well of Ascension (Mistborn 2), Brandon Sanderson
হরিদাস পালেরা...
ঔপনিবেশিক হিন্দু আইন : ২ - এলেবেলে | ১৭৭৬ সালে হ্যালহেডের আইনটি চালু করার সময়ে, ইংরেজরা রাজস্ব ব্যবস্থা নিয়ে নানা পরীক্ষানিরীক্ষা চালালেও কোনও স্থায়ী সমাধানের উপায় খুঁজে পায়নি। বরং এই আমলে অস্বাভাবিক হারে রাজস্ব আদায়ের কারণে, বাংলা ও বিহারের কতিপয় ক্ষমতাশালী রাজা ও জমিদার যে তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করে, তা আমরা আগের পর্বে দেখেছি। কিন্তু প্রথমে হ্যালহেডের আইন ও পরে ১৭৯৩-এ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের ফলে, এই জমিদারশ্রেণি ক্রমে শাসকের প্রতি বৈরী মনোভাব পরিত্যাগ করে তাদের প্রধান সমর্থক হয়ে ওঠে। প্রশাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে এই বৃহত্তম প্রভাবশালী অংশটিকে পারস্পরিক স্বার্থসূত্রে নিজেদের পক্ষে নিয়ে আসার পরে, ঔপনিবেশিক শাসকরা সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হিসাবে নারীদের আর্থিক ও সামাজিকভাবে আরও প্রান্তিক করে দেওয়ার জন্য তোড়জোড় শুরু করে।এই পরিস্থিতিতে হ্যালহেডের A Code of Gentoo Laws-এর ২০ বছরের মধ্যেই ব্রিটিশ শাসকরা দ্বিতীয় একটি আইন তৈরি করার প্রয়োজন অনুভব করে। দ্বিতীয় আইনটির মাধ্যমে ভারতবর্ষের হিন্দু বা মুসলমান প্রজাদের ন্যায়বিচার দেওয়ার বিষয়ে তাদের বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা ছিল না। বরং এই ২০ বছরের মধ্যে তারা প্রচলিত রাজস্ব ব্যবস্থায় যে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটায় এবং সেই পরিবর্তনের ফলে ভারতীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক জগতে যে বিপুল রদবদল ঘটে, তার সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখাই ছিল এই নতুন আইন প্রবর্তনের একমাত্র প্রেরণা।কোম্পানির শাসকবর্গের এই মনোভাবকে আইনের মাধ্যমে প্রতিফলিত করার জন্য, হেস্টিংসের আমলে ১৭৮১ সালে পাস হয় নতুন আইন ‘The Act of Settlement’। এই আইনের ১৭ সংখ্যক ধারায় বলা হয়: “সম্পত্তির উত্তরাধিকার ও জমির উত্তরাধিকার সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় এবং দু-পক্ষের মধ্যে চুক্তি ও লেনদেনের সমস্ত বিষয়, মুসলমানদের ক্ষেত্রে মুসলমান আইন ও ব্যবহার এবং হিন্দুদের ক্ষেত্রে হিন্দু আইন ও ব্যবহার দ্বারা নির্ধারিত হবে।” [১] প্রধানত সম্পত্তির উত্তরাধিকারের বিষয়টিই যে এই আইন প্রবর্তনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, আইনের এই ধারাটি থেকে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেটলমেন্ট অ্যাক্ট পাশ হওয়ার পরে, ১৭৮৩-র ২৫ সেপ্টেম্বর সুপ্রিম কোর্টের পিউনি জজ (puisne judge) হিসাবে কলকাতায় পদার্পণ করেন উইলিয়াম জোন্স। [২] এবার তিনি শাসকের কাঙ্ক্ষিত আইনটি প্রবর্তনের কাজে নিজেকে সমর্পণ করেন। অবশ্য তার আগেই তিনি আদালতে নিযুক্ত জজপণ্ডিতদের বিচারকে উল্টে দিয়ে তাঁর নিজস্ব রায়দান প্রক্রিয়া শুরু করে দেন।১৭৮৫ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর, জজপণ্ডিতদের যোগ্যতার ওপর চূড়ান্ত অনাস্থা প্রকাশ করে চার্লস চ্যাপমানকে তিনি জানান: “এই নিরিবিলি জায়গায় [কৃষ্ণনগর] আমি ধীরগতিতে কিন্তু নিশ্চিতভাবে সংস্কৃত অধ্যয়নের বিষয়ে অগ্রসর হচ্ছি। কারণ আমি আর আমাদের [আদালতের] পণ্ডিতদের— যারা তাদের খেয়ালখুশি মতো হিন্দু আইন পরিচালনা করে— দয়াদাক্ষিণ্য সহ্য করতে পারি না...।” [৩] একই মনোভাব প্রকাশ করে ১৭৮৭-র ১৬ অগস্ট জন শোরকে (পরবর্তীকালে যিনি ভারতবর্ষের তৃতীয় গভর্নর জেনারেল হবেন) জোন্স লেখেন: “...আমি আরবি ও সংস্কৃত অধ্যয়ন করে আদালতকে সহায়তা করছি এবং এখন আমাদের ওপর মুসলমান বা হিন্দু আইনজীবীদের ভুল মতামত চাপিয়ে দেওয়াকে অসম্ভব করে দিয়েছি।” [৪] পরের বছরের ১৯ মার্চ লর্ড কর্নওয়ালিসকেও একই কথা বলেন তিনি: “...যদি আমরা [বিচার সম্পর্কে] কেবল দেশীয় আইনজীবী ও পণ্ডিতদের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকি, তাহলে তাদের দ্বারা [আমরা] যে প্রবঞ্চিত হতে থাকব না, সে বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না।” [৫] সংস্কৃতের পকড় নিয়ে যখন একের পর এক দাম্ভিক উচ্চারণ করছেন জোন্স, তখন তাঁর সংস্কৃত শিক্ষার বয়স সাকুল্যে দু-বছরও পার হয়নি।এই সুযোগে এহেন উইলিয়াম জোন্সের সংস্কৃত চর্চার সামান্য হদিশ নেওয়া যাক। জোন্স লন্ডনে নানা ভাষা শিখলেও সংস্কৃত জানতেন না। কলকাতায় আসার আগে অক্সফোর্ডে শিক্ষক রেখে আরবি শিখেছেন তিনি— এমনটা অবশ্য জানা গেছে। ১৭৮৩ সালে তিনি সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হয়েছেন বটে, অথচ তখনও অবধি সংস্কৃতর ‘স’ জানেন না। ফলে মুনশিদের দিয়ে আরবি, ফারসি আর হিন্দুস্থানি মারফত কাজ চালিয়ে নিচ্ছেন কোনও ক্রমে। ১৭৮৩-র ২৫ সেপ্টেম্বর কলকাতায় আসা ইস্তক সংস্কৃত নিয়ে তাঁর কোনও উৎসাহের কথা জানা তো যাচ্ছেই না, বরং উইলকিন্সকে ১৭৮৪-র ২৪ এপ্রিল তিনি জানাচ্ছেন ‘life is too short and my necessary business too long for me to think at my age of acquiring a new language’। [৬] এদিকে আদালতে সংস্কৃত শাস্ত্রবিচার করে রায় দিতে হয়, জোন্সের যাকে বলে একেবারে বেইজ্জত অবস্থা। হিন্দু শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের খপ্পর থেকে নিজেকে বাঁচাতে ১৭৮৫ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি, তিনি উইলিয়াম পিট (জুনিয়র)-কে জানান তাঁর সংস্কৃত শেখার আসল মনোবাসনার কথা। ভাষা হিসাবে সংস্কৃত শেখা তাঁর উদ্দেশ্যে নয়, আসলে তিনি ভাষাটা শিখতে আগ্রহী যাতে তিনি ‘may be a check on the Pundits of the court’। [৭]এর আগে অর্থাৎ ভারতবর্ষে পদার্পণ করার প্রায় বছর খানেকের মধ্যে, এই উদ্দেশ্যে তিনি কাশীতে হাজির হন। যদিও সেখান থেকে তাঁকে ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরতে হয়। এবারে ১৭৮৫-র সেপ্টেম্বর মাসে, তিনি সংস্কৃত শিক্ষায় হাতে খড়ি নিতে পাড়ি জমান নবদ্বীপ। ৮ সেপ্টেম্বর প্যাট্রিক রাসেলকে চিঠি লিখে তিনি জানাচ্ছেন, সেখানে তাঁর যাওয়ার একমাত্র কারণ হল এমন একজন উপযুক্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সন্ধান করা, যাঁর থেকে তিনি ‘the rudiments of that venerable and interesting language’ [৮] আয়ত্ত করে স্মৃতিশাস্ত্র অনুবাদ করতে পারেন। কিন্তু তাঁর বয়ান অনুযায়ী দুর্গাপুজোর কারণে নবদ্বীপের ব্রাহ্মণেরা তখন নবদ্বীপ ছেড়ে দূরস্থ যজমানদের বাড়িতে চলে গেছেন।যদিও এ বিষয়ে জোন্স যে প্রকৃত সত্যকে আড়াল করেন, সেই তথ্য সম্প্রতি প্রকাশিত রাজেশ কোছারের Sanskrit and the British Empire গ্রন্থ থেকে জানা যায়। কোছারের গবেষণা অনুযায়ী ১৭৮৫ সালে দুর্গাপুজো অক্টোবরের প্রথম দিকে শুরু হয়। কাজেই নবদ্বীপের বিশিষ্ট ব্রাহ্মণদের দুর্গাপুজোর প্রায় তিন সপ্তাহ আগে তাঁদের যজমানদের বাড়িতে চলে যাওয়ার কোনও কারণ থাকতে পারে না। [৯] তা ছাড়া গোটা নদীয়া জেলায় জোন্সের জন্য কোনও সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণকে পাওয়া যায়নি, এ কথাও বিশ্বাস করা কঠিন। বিশেষত যেখানে জোন্সের মতো উচ্চপদস্থ ঔপনিবেশিক কর্মকর্তার পক্ষে অন্তত একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পাওয়ার বিষয়টি অতি সাধারণ ঘটনা হিসাবে বিবেচিত হওয়ার কথা। সম্ভবত কোনও ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তাঁকে সংস্কৃত শেখাতে রাজি না হওয়ার ফলে জোন্স বাধ্য হয়ে এ ব্যাপারে পুজোর অজুহাত দেন।যাই হোক, অনেক চেষ্টা করেও শিক্ষক হিসাবে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের কাউকে না পেয়ে তিনি অব্রাহ্মণ (বৈদ্য) রামলোচন পণ্ডিতকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতা ফেরেন। কৃষ্ণনগর থেকে ১৭ সেপ্টেম্বর লেখা চিঠিতে উইলকিন্সকে জোন্স জানাচ্ছেন, তিনি এবারে রামলোচনের থেকে হিতোপদেশ পড়া শিখবেন। [১০] শুধু তাই নয়, রামলোচনের যাদুগুণে মাত্র এক বছরের মধ্যে তিনি সংস্কৃততে এত পারদর্শী হয়ে ওঠেন যে, ১৭৮৬ সালের ২৩ অক্টোবর জোন্স হেস্টিংসকে জানান, তিনি হিতোপদেশ -এর অনুবাদ করে ফেলেছেন এবং কিছু দিন পরেই ‘compiling a complete Digest of Indian laws’ [১১] -এর কাজে হাত দেবেন।হেস্টিংসকে চিঠি লেখার মাসছয়েক আগে, ওই বছরের ৬ মে স্যার জন ম্যাকফারসনকে লেখা চিঠিতে এই বিষয়ের বিশদ বিবরণ দিয়ে চট্টগ্রাম থেকে জোন্স জানান: “ভারতবর্ষের হিন্দু ও মুসলমানদের বিচারব্যবস্থা সম্পর্কিত একটি সম্পূর্ণ গ্রন্থ আমার দেশবাসীকে উপহার দেব— এই আমার আন্তরিক ইচ্ছা। এই ইচ্ছার বশে আমি বহু দিন থেকে পরিশ্রম করছি। এ সম্পর্কে অশুদ্ধ ফারসি তরজমায় লিখিত একটি গ্রন্থের সাহায্যে আমি প্রাচীনতম সংস্কৃত আইনবিষয়ক গ্রন্থগুলি পাঠ করতে সক্ষম হয়েছি। গত বছর আমি সর্বশ্রেষ্ঠ আরবি আইনগ্রন্থ অনুবাদ করেছি। [বর্তমানে] আমি ইংরেজিতে মনু অনুবাদ করা শুরু করেছি। আমার একার দ্বারা যা সম্ভব, ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমি তা সম্পূর্ণ করব এবং এ বিষয়ে আমি মন্ত্রী, চ্যান্সেলর, বোর্ড অব কন্ট্রোল ও ডিরেক্টরদের লিখব। ...যাঁরা আমাকে জানেন না, তাঁরা মনে করতে পারেন যে আমি ভারতবর্ষের জাস্টিনিয়ান হওয়ার উদ্দেশ্যে বা অর্থের লোভে এই কাজে অবতীর্ণ হয়েছি। কিন্তু কেবল সাধারণের সুবিধা ও উপকার করতে পারব, এই আনন্দটুকু ছাড়া অন্য কোনও পার্থিব সুবিধা লাভের আকাঙ্ক্ষায় আমি এই ধরণের কাজে হস্তক্ষেপ করিনি।” [১২] যে জোন্স ১৭৮৫ সালে সংস্কৃত শিখতে শুরু করেন, সেই একই ব্যক্তি অজ্ঞাত যাদুমন্ত্রে পরের বছরেই মনু অনুবাদ করা শুরু করে দেন! এহ বাহ্য, ‘ভারতবর্ষের হিন্দু ও মুসলমানদের বিচারব্যবস্থা সম্পর্কিত একটি সম্পূর্ণ গ্রন্থ’ তাঁর দেশবাসীকে উপহার দেওয়ার বিষয়টিও তাঁর অন্যতম বাসনা হয়ে ওঠে। তবুও নিছক শাসক পক্ষের লোক হওয়ার দৌলতে, এহেন ‘আইনজ্ঞ’ ও ‘সংস্কৃতজ্ঞ’ জোন্স যে শাসকদের নয়নের মণি হবেন, সে তো জানা কথা। তাই তাঁর ওপরই অর্পিত হয় হিন্দু ও মুসলমানদের জন্য দুটি নতুন আইন বানানোর দায়িত্ব। আর জোন্সও শাসকের বাঞ্ছিত আইন প্রণয়নের কাজে আদাজল খেয়ে লেগে পড়েন।দায়িত্ব পেয়েই তাঁর পূর্বসুরী হ্যালহেডের আইনটির অনুবাদের বিষয়ে নানাবিধ ত্রুটি আবিষ্কারে ব্যস্ত হয়ে পড়েন জোন্স। তাঁর অনূদিত মনুসংহিতা-র ভূমিকায় তিনি লেখেন, এই নতুন আইন প্রবর্তনের ক্ষেত্রে তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য হল যাবতীয় ‘natural defects in the old jurisprudence of this country’-কে বিদায় করে তাকে ‘accommodate it justly to the improvements of a commercial age’ [১৩] করা। তবে হ্যালহেডও যেহেতু শাসক পক্ষের লোক, সেহেতু আগের আইনটির যাবতীয় ত্রুটিবিচ্যুতির দায়ভার তিনি ফারসি অনুবাদকদের ওপর চাপিয়ে দেন। লক্ষণীয়, হ্যালহেড তাঁদের ওপর যে এই দোষারোপ করেননি, তা তাঁর লিখিত ভূমিকাতে স্পষ্ট। কিন্তু জোন্স শুধু আদালতের সরকারি জজপণ্ডিতদের ওপর অবিশ্বাস জ্ঞাপনই করেন না, ফারসি অনুবাদকরাও তাঁর অবিশ্বাসের আওতায় চলে আসতে বাধ্য হন।১৭৮৮ সালের ১৯ মার্চ গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিসকে লেখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চিঠিটিতে জোন্স বলেন: “...যদিও হ্যালহেড বিশ্বস্ততার সঙ্গে তাঁর ভূমিকা পালন করেছিলেন, তবুও [ভাষান্তরের সময়ে] তিনি যে ফারসি অনুবাদ ব্যবহার করেন, তার সঙ্গে মূল সংস্কৃতের অনেক পার্থক্য আছে। [এই আইনে] অনেকগুলি প্রয়োজনীয় অনুচ্ছেদ বাদ দেওয়া হয়েছে, যদিও [মূল] পাঠ্যটি ব্যাখ্যা করা বা উন্নত করার জন্য নিরর্থকভাবে তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ কিছু টীকা সংযোজিত হয়েছে।” [১৪] চিঠিটির এই অংশ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায়, হ্যালহেডের আইনটিতে মূল সংকলন গ্রন্থ থেকে অনুবাদের সময়ে প্রচুর সংযোজন-বিয়োজন ঘটে। এই ত্রুটির জন্য জোন্স যতই ফারসি অনুবাদকদের দায়ী করুন না কেন, শাসকের গোপন মনোভাব আর গোপন থাকে না।নতুন আইনটি চালু করার ক্ষেত্রে শাসকের মূল উদ্দেশ্য ছিল— ক) নারীদের সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করে সমাজে তাঁদের ব্রাত্য ও প্রান্তিক করে দেওয়া ও খ) তাঁদের জীবনধারণের জন্য কেবল পুরুষদের কৃপার ওপর নির্ভরশীল করে তোলা। তাই অত্যন্ত পরিকল্পিভাবে জোন্স তাঁর আইনের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ হিসাবে নারীদের চূড়ান্ত অবমাননাকারী পিতৃতান্ত্রিক মনুকে বেছে নেন। মনুকে কেবল ‘son or grandson of BRAHMA’ বলেই নিশ্চিন্ত হতে পারেন না জোন্স, বরং মনুসংহিতা-কে আপামর হিন্দুর কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য, তাঁকে চিহ্নিত করেন ‘not the oldest only, but the holiest of legislators’ [১৫] রূপেও।মনুসংহিতা নারীদের সম্পর্কে এত পরস্পরবিরোধী ও অশ্লীল উক্তিতে ভর্তি, যা থেকে সহজেই বোঝা যায় সমাজকর্তারা তাঁদের প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন সময়ে এই ধর্মশাস্ত্রটিতে প্রচুর সংযোজন ও বিয়োজন ঘটিয়েছিলেন। এত বিচ্যুতি সত্ত্বেও গ্রন্থটিতে নারীদের জন্য যে সামান্য অধিকারটুকু বজায় ছিল, তাকেও সমূলে উৎপাটিত করতে উদ্যোগী হন জোন্স। মনুসংহিতা-র বিভিন্ন অধ্যায়ে বিবৃত নানা শ্লোক এবং জোন্সের সূক্ষ্ম সুকৌশলী কারিকুরির বিশদ আলোচনা করলে, বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে। তবে এই বিষয়ে প্রথমে আমরা মনুসংহিতা-তে নারী সম্পর্কে পরস্পরবিরোধী শ্লোকের নমুনা দেখব।উদাহরণস্বরূপ, তৃতীয় অধ্যায়ে যে মনু নারীকে সম্মান দেন এই উক্তি করে:যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ।। ৩. ৫৬(যে কুলে স্ত্রীলোকেরা পূজিত হন, সেখানে দেবতারা প্রসন্ন হন। আর যে কুলে এঁদের অনাদর হয়, সে বংশে সকল কর্ম নিষ্ফল হয়)। [১৬] সেই একই মনু নবম অধ্যায়ে অবলীলায় লেখেন:নৈতা রূপং পরীক্ষন্তে নাসাং বয়সি সংস্থিতিঃ।সুরূপম্বা বিরূপম্বা পুমানিত্যেব ভুঞ্জতে।। ৯.১৪(স্ত্রীরা রূপ বিচার করে না, যুবক বা বৃদ্ধ তা-ও দেখে না, সুরূপ বা কুরূপ হোক, পুরুষ পেলেই তার সঙ্গে সম্ভোগ করে)। [১৭] তিনি লিখতে পারেন:শয্যাসনমলঙ্কারং কামং ক্রোধমনার্জ্জবম্।দ্রোহভাবং কুচর্য্যাঞ্চ স্ত্রীভ্যো মনুরকল্পয়ৎ।। ৯.১৭(শয়ন, উপবেশন, অলংকার, কাম, ক্রোধ, কুটিলতা, পরহিংসা, ঘৃণিত আচরণ— সৃষ্টিকালে এইগুলি স্ত্রীলোকের [স্বভাবগত করে] মনু স্বয়ং কল্পিত করেছেন)। [১৮] সুতরাং মনুর মতে, নারী ক্রোধী, কুটিল ও হিংসুটে। তাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, অলংকারের লোভ ও বয়স নির্বিশেষে পুরুষদের প্রতি ঝোঁক।চূড়ান্ত পিতৃতান্ত্রিকতার পূজারী মনু নারীদের এতটাই অবিশ্বাস করেন যে, একাকী পুরুষকে জননী, ভগ্নী এমনকি কন্যার সঙ্গেও নির্জন গৃহে বাস করতে নিষেধ করে দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিনি বলেন:স্বভাব এষ নারীণাং নরাণামিহ দূষণম্।অত[হো]র্থান্ন প্রম্যাদন্তি প্রমদাসু বিপশ্চিতঃ।।অবিদ্বাংসমলং লোকে বিদ্বাংসমপি বা পুনঃ।প্রমদা হুৎপথং নেতুঃ কামক্রোধবশানুগম্।।মাতা স্বস্রা দুহিত্রা বা ন বিবিক্তাসনো ভবেৎ।বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি।। ২. ২১৩-১৫(পুরুষদের দূষিত করাই নারীদের স্বভাব, তাই পণ্ডিতেরা নারী সম্পর্কে কখনও অমনোযোগী হন না। কোনও পুরুষ নিজেকে বিদ্বান মনে করে নারীর নিকট বাস করবেন না, যেহেতু কামক্রোধের বশীভূত নারী বিদ্বান-অবিদ্বান নির্বিশেষে পুরুষকে অনায়াসে উন্মার্গগামী করতে সমর্থ হয়। যেহেতু শক্তিশালী ইন্দ্রিয়সমূহ বিদ্বান ব্যক্তিকেও বশীভূত করে, সেহেতু মা, বোন বা মেয়ের সঙ্গেও পুরুষ নির্জন গৃহে থাকবে না)। [১৯] সহজ কথায়, কেবল নারী হওয়ার অপরাধে মা, বোন কিংবা মেয়ে কাম-ক্রোধের বশবর্তী হয়ে ছেলে-ভাই-বাবাকে বশীভূত করে বিপথে নিয়ে যেতে পারে।মনুর মতে স্বামী দুশ্চরিত্র হতে পারেন, কামুক হতে পারেন। তা সত্ত্বেও স্ত্রী তাঁকেই দেবতার মতো সেবা করবেন:বিশীলঃ কামবৃত্তো বা গুণৈর্ব্বা পরিবর্জ্জিতঃ।উপচর্য্যঃ স্ত্রিয়া সাধ্ব্যা সততং দেববৎ পতিঃ।। ৫. ১৫৪(পতি সদাচারবিহীন, কামুক বা গুণহীন হলেও সাধ্বী স্ত্রী সর্বদা দেবতার ন্যায় পতির সেবা করবে)। [২০] আর সেই ‘দেবতার ন্যায় পতি’ মারা গেলে স্ত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট হবে এই শ্লোকটি:কামন্তু ক্ষপয়েদ্দে[হং] পুষ্পমূলফলৈঃ শুভৈঃ।ন তু নামাপি গৃহ্নীয়াৎ পত্যৌ প্রেতে পরস্য তু।। ৫. ১৫৭(পতি মৃত হলে স্ত্রী পবিত্র ফুল-ফল-মূলাদি খেয়ে দেহ ক্ষীণ করবেন, কিন্তু পরপুরুষের নামগ্রহণও করবেন না)। [২১] শুধু তাই নয়, এ বিষয়ে মনু আরও নির্দেশ দেন:অপত্যলোভাদ্ যা তু স্ত্রী ভর্ত্তারমতিবর্ত্ততে।সেহ নিদামবাপ্নোতি পতিলোকাচ্চ হীয়তে। ৫. ১৬১(স্ত্রীলোক ব্যভিচার দ্বারা সন্তান উৎপাদন করবেন না, তা করলে তিনি ইহকালে নিন্দিত হন এবং পরলোকে সেই পুত্র দ্বারা স্বর্গলাভ হয় না)। [২২] মনুর কাছে স্ত্রী সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র মাত্র, সন্তান উৎপাদন ছাড়া তার স্বতন্ত্র সত্তা থাকতে পারে না বলে তিনি মনে করেন। তাই গর্ভবতী স্ত্রীর প্রশংসা করে তিনি জানান:প্রজনার্থং মহাভাগাঃ পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ।স্ত্রিয়ং শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষো[হ]স্তি কশ্চন।। ৯.২৬(স্ত্রীর গর্ভধারণ অতিশয় মঙ্গলকারক, এজন্য তারা বস্ত্রালঙ্কারাদি প্রদানে বহু সম্মানের যোগ্য ও গৃহের শোভাজনক হয়, এমনকি স্ত্রী ও শ্রী— উভয়ের মধ্যে কোনও ভেদ নেই। নিঃশ্রীক গৃহ যেমন শোভা পায় না, নিঃস্ত্রীক গৃহও তেমন শোভা পায় না)। [২৩] অন্য দিকে পতি কেমন হবেন, সে সম্পর্কে মনু বলেন:ভার্য্যায়ৈ পূর্ব্বমারিণৈ দত্ত্বাগ্নীনন্ত্যকর্ম্মণি।পুনর্দ্দারক্রিয়াং কুর্য্যাৎ পুনরাধানমেব চ।। ৫. ১৬৮(সুশীলা ভার্যা আগে মারা গেলে তার দাহকার্য সম্পন্ন করে পুরুষ পুনরায় বিবাহ করবেন অথবা শ্রৌত বা স্মার্ত অগ্নি গ্রহণ করবেন)। [২৪] নারীকে বিধবা হওয়ার পর কঠোর ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে দেহ ক্ষয় করার নির্দেশ দেন মনু, অথচ পুরুষকে পত্নী মারা গেলে তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করার পরেই নতুন পত্নী গ্রহণ করার অনুমতি দেন। আর নারীদের অবমাননাকারী এই পিতৃতান্ত্রিক মনুকেই গুরুঠাকুর ঠাউরান জোন্স।কিন্তু জোন্স কি সত্যিই মনুকে খুব শ্রদ্ধার চোখে দেখেন? মনুসংহিতা-কে আইনে রূপান্তরিত করার সময়ে তিনি কি সত্যিই মনুর উল্লিখিত নির্দেশাবলীকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন? ১৭৯৪ সালে তিনি Institutes of Hindu Law: Or, the Ordinances of Menu, According to the Gloss of Culluca নামে মনুসংহিতা-র যে অনুবাদ করেন, সেই গ্রন্থের ভূমিকাতে মনুর প্রতি জোন্সের এই শ্রদ্ধাশীল দৃষ্টিভঙ্গির কোনও নিদর্শন আদৌ মেলে না। বরং সেখানে তিনি সোজাসুজি মনুস্মৃতিকে ‘system of despotism and priestcraft’ বলে চিহ্নিত করে স্পষ্ট লেখেন: “…it is filled with strange conceits in metaphysics and natural philosophy, with idle superstitions, and with a scheme of theology most obscurely figurative, and consequently liable to dangerous misconception; it abounds with minute and childish formalities, with ceremonies generally absurd and often ridiculous; the punishments are partial and fanciful….” [২৫] তবুও কেবল শাসকের সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে মনুসংহিতা-কে ‘the most venerable text in the Indian scripture’ ও ‘those laws are actually revered, as the word of Most High’ [২৬] বলে, তাকেই আইন হিসাবে চিহ্নিত করেন তিনি।হিন্দু আইনের সংকলন গ্রন্থটির জন্য জোন্স অনুবাদক ও লিপিকর হিসাবে কাদের নিযুক্ত করেছিলেন, ১৭৮৮ সালের ১৩ এপ্রিল লর্ড কর্নওয়ালিসকে লেখা জোন্সের অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ চিঠি থেকে সে বিষয়ে বিশদে জানা যায়। সেই চিঠিতে কর্নওয়ালিসকে জোন্স জানান, হিন্দু আইনের জন্য তিনি বাংলার পণ্ডিত রাধাকান্ত শর্মা ও বিহারের পণ্ডিত সবুর তিওয়ারি এবং লিপিকররূপে মহতাব রায়কে নির্বাচিত করেছেন। [২৭] আসলে জোন্সের মূল পরিকল্পনা ছিল, মিতাক্ষরা ও দায়ভাগের জন্য দুটি আলাদা সংকলন গ্রন্থ তৈরি করা। সেই অনুযায়ী সবুর তিওয়ারি (পাঠান্তরে সর্বরী ত্রিবেদী) ১৭৮৯ সালে বিবাদসারার্ণব নামে একটি সংকলন প্রস্তুত করেন। কিন্তু এটি প্রকাশিত হয়নি, অনূদিত হয়নি এমনকি কখনও সুপ্রিম কাউন্সিলে পাঠানোও হয়নি। ইতিমধ্যে ১৭৮৮-র অগস্ট মাসে একটি নতুন সংকলন গ্রন্থের জন্য জোন্স ত্রিবেণীর কিংবদন্তি সংস্কৃত পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। [২৮] অবশেষে ওই বছরের ২২ অগস্ট, কর্নওয়ালিসের অনুমতিক্রমে মাসিক ৩০০ টাকা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননকে নিযুক্ত করেন জোন্স। [২৯]জোন্স যে সরকারিভাবে ‘হিন্দু’ আইন সংকলন করার পাশাপাশি ‘মুসলমান’ আইন সংকলন করার দায়িত্বও পান— সে কথা আগেই বলা হয়েছে। এ বিষয়ে তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল কর্নওয়ালিসকে ১৭৮৮-র ১৯ মার্চ লেখা দীর্ঘ চিঠিতে তাঁর পরিকল্পনার কথা বিশদে জানিয়ে জোন্স লেখেন: “বহু দিন থেকেই আমার বাংলা ও বিহারের বিচারবিভাগের দিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার ইচ্ছা ছিল। ...হিন্দু ও মুসলমান— এই দুই সম্প্রদায়ের মামলা-মোকদ্দমা নিজ নিজ সম্প্রদায়ের বিশেষ বিধিব্যবস্থা অনুযায়ী নিষ্পন্ন হওয়াই বাঞ্ছনীয়, কারণ তারা তাদের আবহমানকাল ধরে প্রচলিত ব্যবস্থাগুলিকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখে এবং একেবারে নতুন কোনও আইনের সাহায্যে তাদের মামলা-মোকদ্দমা নিষ্পত্তির ব্যবস্থা প্রচলিত হলে, তারা অত্যন্ত নিপীড়িত হচ্ছে বলে মনে করতে পারে। ...হিন্দু ও মুসলমানদের বিধিব্যবস্থাগুলি প্রধানত সংস্কৃত ও আরবি— এই দুই কঠিন ভাষার শৃঙ্খলে আবদ্ধ। খুব কম ইউরোপীয়ই এই ভাষা শিক্ষা করবে, কারণ এর মাধ্যমে তাদের কোনও পার্থিব লাভ হবে না। অথচ যদি আমরা [বিচার সম্পর্কে] কেবল দেশীয় আইনজীবী ও পণ্ডিতদের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকি, তাহলে তাদের দ্বারা [আমরা] যে প্রবঞ্চিত হতে থাকব না, সে বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না।” [৩০]জোন্স যাঁদের মুখাপেক্ষী থাকতে চান না, অতঃপর সেই পণ্ডিত ও মৌলবিদেরই কাজে লাগিয়ে নতুন সংকলন গ্রন্থ তৈরি করার বাসনা নিয়ে একই চিঠিতে তিনি জানান: “[রোম সম্রাট] জাস্টিনিয়ানের ব্যবস্থাশাস্ত্র (Digest)-কে আদর্শ করে আমরা যদি এ দেশীয় বিজ্ঞ আইনজীবীদের সাহায্যে হিন্দু ও মুসলমান বিচারব্যবস্থার একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ সংকলিত করাই এবং যথাযথভাবে তার ইংরেজিতে অনুবাদ করিয়ে এক এক খণ্ড সদর দেওয়ানি আদালত ও সুপ্রিম কোর্টে রেখে দিই, তাহলে বিচারকেরা [তাঁদের] প্রয়োজন মতো এই সংকলন গ্রন্থ দেখতে পারবেন; ফলে পণ্ডিত বা মৌলবিরা আমাদের ভুল পথ দেখাচ্ছে কি না, তা ধরা সহজ হবে। ...আমাদের এই সংকলনের কাজ অল্প সময়ের মধ্যেই শেষ হবে। আমরা কেবল উত্তরাধিকারী এবং চুক্তি-সংক্রান্ত আইনগুলি সংকলন করতে চাই, কারণ সচরাচর এই দুই ধরনের মামলাই বেশি হয়। ...আপাতত এই কাজের জন্য খুব কঠিন পরিশ্রমও করতে হবে না। এ সম্পর্কে সংস্কৃত ও আরবি ভাষায় দুটি গ্রন্থ আছে। তার প্রথমটি কয়েক শতাব্দী আগে এই প্রদেশেরই রঘুনন্দন নামে একজন ব্রাহ্মণ প্রণয়ন করেন...। দ্বিতীয়টি বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের হুকুমে তাঁরই রাজত্বকালে ‘ফতোয়া-ই-আলমগিরি’ নামে পাঁচটি খণ্ডে সংকলিত হয়— আমার কাছে যার একটি নিখুঁত এবং সুসংহত অনুলিপি আছে। [এ ছাড়া] ...হেস্টিংসের অনুরোধক্রমে হিন্দু আইনের যে গ্রন্থ সংকলিত হয়েছিল, সেটিও একই উদ্দেশ্যে কার্যকর হবে।” [৩১] যদিও তাঁর সংকলিত ও অনূদিত গ্রন্থে জোন্স রঘুনন্দনের দায়তত্ত্ব-কে সামান্যতম গুরুত্ব না দিয়ে হ্যালহেডের আইন সংকলনটির ওপর যাবতীয় গুরুত্ব আরোপ করেন।চিঠিটিতে তিনি যে সম্ভাব্য ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন, তা থেকে জানা যায় হিন্দু ও মুসলমানদের পৃথক আইনের জন্য নির্বাচিত গ্রন্থগুলির সংকলন ও অনুবাদের জন্য দুজন পণ্ডিত, দুজন মৌলবি— একজন শিয়া ও অন্যজন সুন্নি সম্প্রদায়ের— এবং দুজন লিপিকরের জন্য পারিশ্রমিক বাবদ যথাক্রমে মাসিক ২০০ টাকা ও ১০০ টাকা হিসাবে মাসে মোট খরচ হবে ১ হাজার সিক্কা টাকা। তবে এই বিশাল অঙ্কের পারিশ্রমিকের লোভে তাঁরা যাতে দীর্ঘদিন এ কাজে ব্যাপৃত না থাকতে পারেন, সেই কারণে তাঁদের কাজটি সম্পন্ন করার সময়সীমাও নির্দিষ্ট করে দিয়ে তিনি চিঠিতে জানান: “তিন বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ সংকলনটি শেষ করে তা লিপিবদ্ধ করতে হবে, যার মেয়াদ শেষ হলে তাদের বেতন বন্ধ হয়ে যাবে।” [৩২] যেহেতু রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কারের মূল বিবাদ-বিসংবাদটি সংস্কৃত ধর্মশাস্ত্রের বিভিন্ন গ্রন্থে বিধৃত শ্লোকসমূহের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়, সেহেতু এই অধ্যায়ে আমরা মুসলমান আইনের বদলে কেবল ধর্মশাস্ত্রের বিভিন্ন গ্রন্থের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা হিন্দু আইনের বিষয়টিতেই আমাদের আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখব।এই গুরুদায়িত্ব পাওয়ার পরে, জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন সংকলন গ্রন্থটিতে হিন্দুদের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত সম্ভাব্য সমস্ত বিষয়ে মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, নারদ, বৃহস্পতি, কাত্যায়ন প্রভৃতি ধর্মবেত্তাদের মতামত উদ্ধৃত করেন। অবশেষে তাঁর সহকারীদের প্রত্যক্ষ সহায়তায়, প্রায় চার বছর (১৭৮৮-১৭৯২) অক্লান্ত পরিশ্রমের শেষে তিনি প্রণয়ন করেন হিন্দু আইনের সংকলন বিবাদভঙ্গার্ণব। কিন্তু গ্রন্থটির অনুবাদ শেষ করার আগেই ১৭৯৪ সালের ২৭ এপ্রিল জোন্স মারা যান। তাঁর অবর্তমানে গভর্নর জেনারেল জন শোরের নির্দেশে হেনরি কোলব্রুক ১৭৯৬-এর ডিসেম্বরে সংকলন গ্রন্থটির অনুবাদ সম্পন্ন করেন। ১৭৯৭ সালে অনুবাদটি A Digest of Hindu Law on Contracts and Successions শিরোনামে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। ঔপনিবেশিক শাসকদের মনোবাঞ্ছা পূরণের উদ্দেশ্যে, এই সংস্কৃত গ্রন্থটি ইংরেজিতে অনুবাদ করার সময়ে মহিলাদের সম্পত্তির উত্তরাধিকার সম্পর্কিত কোন অংশটিতে জোন্স অতিরিক্ত নিজস্ব ব্যাখ্যা সংযোজন করেন, তা আমরা পরবর্তী আলোচনাতে দেখতে পাব।মহিলাদের ক্ষেত্রে জোন্সের এহেন পক্ষপাতমূলক আচরণেরও নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা বর্তমান। ব্রিটিশ শাসকদের দ্বিতীয় আইনটি চালু করার মূল উদ্দেশ্যই ছিল মহিলাদের সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা। এ কথা ঠিক, জোন্সের এই পরিকল্পনার ক্ষেত্রে যাবতীয় আর্থিক দায়ভার বহন করার সরকারি অনুমতি দেন লর্ড কর্নওয়ালিস। তবে যে সময়ে এই অনুবাদকর্মটি সমাপ্ত হয় (ডিসেম্বর ১৭৯৬), তত দিনে ভারতবর্ষের তৃতীয় গভর্নর জেনারেল জন শোর প্রশাসনিক ক্ষমতায় এসে গেছেন। এমনকি গভর্নর জেনারেল হওয়ার আগেও তাঁর মনোভাব যে এ বিষয়ে তাঁর পূর্ববর্তী শাসকদের থেকে আলাদা কিছু ছিল না, তারও একাধিক নিদর্শন পাওয়া যায়।সম্পত্তি পরিচালনার ক্ষেত্রে মহিলাদের অযোগ্য মনে করে শোর তাদের ‘passive instruments’ রূপে সংজ্ঞায়িত করেন এবং মহিলাদের পরিবর্তে কোনও পুরুষ কর্মচারী বা মহিলাদের পুরুষ আত্মীয়স্বজনদের সেই দায়িত্ব পালনের পক্ষে মতপ্রকাশ করেন। এ বিষয়ে তিনি স্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করে লেখেন: “আমি মহিলা জমিদারদের সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করব, যা তাদের [সম্পত্তি] পরিচালনার বিরুদ্ধে আপত্তিগুলিকে শক্তিশালী করে সম্ভবত একটি নিয়মের প্রয়োজনীয়তার পরামর্শ দেবে এবং তারা [রাজস্ব] সংগ্রহের বিষয়ে অক্ষম বলে ঘোষণা করবে। ...তারা তাদের কর্মচারীদের কাছে নিছকই নিষ্ক্রিয় যন্ত্র মাত্র এবং তাদের প্রধান ব্যক্তি হিসাবে উপস্থাপিত করা হলেও [তারা] অধিকাংশ ক্ষেত্রে লেনদেন সম্পর্কে অজ্ঞ।” [৩৩] এ প্রসঙ্গে জন শোর মনুর বিখ্যাত শ্লোক ‘পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে’-এর উল্লেখ করে নারীদের সম্পত্তির অধিকারের ক্ষেত্রে মহিলা জমিদারদের ‘disqualified from management and interference in the collections’ [৩৪] বলে ঘোষণা করেন।হেস্টিংস, হ্যালহেড, কর্নওয়ালিস ও জন শোরের পদাঙ্ক অনুসরণ করে জোন্স তাঁর অনুবাদের একটি ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধন করে নারীদের সম্পত্তির উত্তরাধিকার সম্পর্কিত হ্যালহেডের রেখে যাওয়া ফাঁকটিকে পুরোপুরি ভরাট করে দেন। মনুসংহিতা-য় লিখিত আছে: ঊর্দ্ধং পিতুশ্চ মাতুশ্চ সমেত্য ভ্রাতরঃ সমম্।ভজেরন্ পৈতৃকং রিকথ্মনীশাস্তে হি জীবতোঃ।। ৯. ১০৪(পিতা ও মাতার মৃত্যুর পরে ভ্রাতৃগণ মিলিত হয়ে পৈতৃক সম্পত্তি ভাগ করবে; কারণ, তাঁরা জীবিত থাকতে পুত্রগণ [সম্পত্তির] অধিকারী নয়)। [৩৫] অথচ এই শ্লোকটির অনুবাদের সময়ে জোন্স অতিরিক্ত ভাষ্য হিসাবে সংযোজন করেন, ‘unless the father chooses to distribute it’। [৩৬] [নজরটান জোন্সের] যদিও পিতা তাঁর সম্পত্তির পরবর্তী উত্তরাধিকারী নির্ধারণের ক্ষেত্রে নিজস্ব পছন্দটি কীভাবে— মৌখিক না লিখিত— ব্যক্ত করবেন, সে বিষয়ে আইনে ইচ্ছাকৃতভাবেই কোনও স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়নি। অতঃপর এই আইনি ফাঁকের সাহায্য নিয়ে, পিতার মৃত্যুর পরে বিধবা স্ত্রীকে তাঁর উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ন্যায্য সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করে তাঁর জীবদ্দশাতেই পুত্ররা নিজেদের মধ্যে পৈতৃক সম্পত্তির ভাগবাঁটোয়ারা করতে শুরু করে।এই গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনটির ফলে যেমন বিধবা স্ত্রীকে তাঁর জীবদ্দশাতেই স্বামীর সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়, তেমনই অবিবাহিতা কন্যাদেরও পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। নবম অধ্যায়ের অন্য একটি শ্লোকে এ বিষয়ে মনু বলেন: স্বেভ্যো[হং]শেভ্যস্তু কন্যাভ্যঃ প্রদদ্যুর্ভ্রাতরঃ পৃথক্।স্বাৎ স্বাদংশাচ্চতুর্ভাগং পতিতাঃ স্যুরদিৎসবঃ।। ৯. ১১৮ভরতচন্দ্র শিরোমণি এই শ্লোকটির দীর্ঘ ব্যাখ্যা করে একদম শেষ বাক্যে জানিয়েছেন: (...পিতার মরণোত্তর পুত্রের ন্যায় অবিবাহিতা কন্যারাও অংশিনী হইবে এবং বিবাহব্যয়ের অবশিষ্ট যাহা থাকিবে, তাহা কন্যারা পাইবে, এরূপ অংশ ভগিনীদিগকে না দিলে পতিত হয়)। [৩৭] কিন্তু জোন্সের অনুবাদের ‘সৌজন্যে’ অবিবাহিতা কন্যারাও এ বিষয়ে যাবতীয় অধিকার হারাতে বাধ্য হন।এইভাবে একে একে দায়ভাগের অনুল্লেখ, বিধবা স্ত্রীর জীবিত অবস্থায় সন্তানদের পিতৃসম্পত্তির বিলিবন্টন, স্ত্রীধনের বিলোপসাধন পর্বের একদম শেষ পর্যায়ে বিধবা স্ত্রী ও অবিবাহিতা কন্যাদের সম্পত্তির ন্যায্য অধিকারের প্রসঙ্গটিকে পুরোপুরি খতম করে দেন জোন্স। মনুসংহিতা ও অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রকে নিছক আত্মরক্ষার ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে নারীদের ওপর নিজস্ব ভাষ্যের তলোয়ারটি সুনিপুণ হস্তে চালনা করেন তিনি, অথচ কোথাও রক্তপাতের সামান্যতম চিহ্নটুকুও দেখা যায় না। (আগামী পর্বে শেষ হবে।)***********************************************************************উল্লেখপঞ্জি:১. Footnote 2, Letter No. 485; Garland Cannon (ed.), The Letters of Sir William Jones, Vol. II, Oxford, 1970, pp. 794-95২. S. N. Mukherjee, Sir William Jones: A Study in Eighteenth-Century British Attitudes to India, Cambridge, 1968, p. 76৩. Letter No 418; Garland Cannon (ed.), The Letters of Sir William Jones, Vol. II, pp. 683-84৪. Letter No 465; তদেব, পৃ. ৭৬২৫. Letter No 485; তদেব, পৃ. ৭৯৫৬. Letter No 388; তদেব, পৃ. ৬৪৬৭. Letter No 396; তদেব, পৃ. ৬৬৪৮. Letter No 416; তদেব, পৃ. ৬৮০৯. Rajesh Kochhar, Sanskrit and the British Empire, New York, 2021, p. 42১০. Letter No 417; Garland Cannon (ed.), The Letters of Sir William Jones, Vol. II, p. 682১১. Letter No 446; তদেব, পৃ. ৭১৮১২. Letter No. 433; তদেব, পৃ. ৬৯৯১৩. William Jones, Institutes of Hindu Law: Or, the Ordinances of Menu, According to the Gloss of Culluca, Calcutta, 1796, p. iv; এরপর কেবল Institutes of Hindu Law লেখা হবে।১৪. Letter No 485; Garland Cannon (ed.), The Letters of Sir William Jones, Vol. II, p. 797১৫. William Jones, Institutes of Hindu Law, p. iv১৬. ভরতচন্দ্র শিরোমণি, মনুসংহিতা, পৃ. ২১৭১৭. তদেব, পৃ. ৭৫৯১৮. তদেব, পৃ. ৭৬০১৯. তদেব, পৃ. ১৭২-৭৩২০. তদেব, পৃ. ৪৬৯২১. তদেব, পৃ. ৪৭০২২. তদেব, পৃ. ৪৭১২৩. তদেব, পৃ. ৭৬৩২৪. তদেব, পৃ. ৪৭৩২৫. William Jones, Institutes of Hindu Law, p. xv২৬. তদেব, p. xvi২৭. Letter No. 487; Garland Cannon (ed.), The Letters of Sir William Jones, Vol. II, p. 802২৮. S. N. Mukherjee, Sir William Jones: A Study in Eighteenth-Century British Attitudes to India, pp. 137-38২৯. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৭২০৩০. Letter No. 485; Garland Cannon (ed.), The Letters of Sir William Jones, Vol. II, pp. 794-95৩১. তদেব, পৃ. ৭৯৫-৯৭৩২. তদেব, পৃ. ৭৯৮৩৩. Shore’s Minute of 18th June 1789; W. K. Firminger (ed.), The Fifth Report from the Select Committee of the House of Commons on the Affairs of the East India Company, Vol. II, Calcutta, 1917, p. 72৩৪. তদেব, পৃ. ৭৩৩৫. ভরতচন্দ্র শিরোমণি, মনুসংহিতা, পৃ. ৭৮৮৩৬. William Jones, Institutes of Hindu Law, p. 258৩৭. ভরতচন্দ্র শিরোমণি, মনুসংহিতা, পৃ. ৭৯৩কিষেণজি মৃত্যু রহস্য - পর্ব ১৯ - বিতনু চট্টোপাধ্যায় | এনকাউণ্টার: শশধর মাহাতো২০১১ সালের মার্চ, সকালবেলা খবরটা এল ঝাড়গ্রাম পুলিশের এক অফিসারের কাছে। এমন খবর আগের ছ’মাসে একাধিকবার এসেছে কয়েকজন অফিসারের কাছে। কোনও খবর কিছুটা ঠিক, কোনওটা নয়। কিন্তু ২০১০ সালের মাঝামাঝি থেকেই ঝাড়গ্রাম পুলিশ একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। একদম জেনুইন মাওয়িস্ট লিডার ছাড়া অন্য কাউকে গ্রেফতার করা হবে না। এমনকী অচেনা, সাধারণ কোনও স্কোয়াড মেম্বার সম্পর্কে খবর এলেও তা অ্যাভয়েড করা হবে আরও বড় টার্গেটের লক্ষ্যে। যদি সম্ভব হয় সাধারণ স্কোয়াড মেম্বারকে না গ্রেফতার করে বুঝিয়ে দিতে হবে, তাঁকে গ্রেফতার করা যেত, কিন্তু তা করা হয়নি। এতে তাঁর মধ্যে কনফিডেন্স তৈরি হবে। এভাবেই পুলিশ যথেষ্ট বিশ্বাস অর্জন করে ফেলেছিল বহু পিসিপিএ নেতা এবং মাঝারি মাপের স্কোয়াড মেম্বারের। তাঁরাই হয়ে উঠেছিলেন পুলিশের সোর্স। ঝাড়গ্রামের এমনই মাওয়িস্ট স্কোয়াডের এক সদস্য এক অফিসারের সোর্স হয়ে উঠেছিলেন। সোর্স কীভাবে তৈরি হয় এবং কীভাবে তাঁকে মেইনটেইন করতে হয়, তা লিখে শব্দ সংখ্যা বাড়িয়ে লাভ নেই। গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এটাই, রাজ্যে পরিবর্তনের বছরে বিধানসভা ভোটের মাসখানেক আগে এক অফিসারের কাছে ফোন এল, ‘স্যার শশধর আজ চাঁনসরা গ্রামে আছে। কাল গেছে ওখানে, আজ সারাদিন থাকবে।’ কিষেণজিকে বাদ দিলে শশধর মাহাতো সেই সময় তো বটেই, তার আগেও সবচেয়ে প্রমিনেন্ট মাওবাদী নেতা। আকাশ, মদন মাহাতোর বয়স হয়েছে, লালগড় আন্দোলন চলাকালীন যত বড়ো ঘটনা মাওবাদীরা ঘটিয়েছে, তার বেশিরভাগেরই নেতৃত্বে ছিলেন শশধর মাহাতো। তাঁর সম্পর্কে খবরটা পেয়েই প্ল্যানিংয়ে বসলেন ওই অফিসার, জানালেন শুধুমাত্র এক সুপিরিয়র অফিসারকে। আলোচনা করে দুপুর আড়াইটে-তিনটে নাগাদ অপারেশনের প্ল্যান করলেন তাঁরা। দুপুরে গ্রাম কিছুটা ফাঁকা থাকে। ঠিক হল, একদম সাদা পোশাকে অল্প কয়েকজন যাবেন চাঁচসরা গ্রামে। বড়ো গাড়ি নয়, মোটরসাইকেলে। সেই অনুযায়ী সিআরপিএফের বাছাই করা কয়েকজন জওয়ানকে নিয়ে এসডিপিও অম্লান কুসুম ঘোষ এবং বিনপুর থানার ওসি সুকোমল দাস রওনা দিলেন চাঁনসরার দিকে। আটটা মোটরসাইকেলে ষোলজন, সবাই সাদা পোশাকে। তখন দুপুর প্রায় ৩ টে। বিনপুর থেকে চাঁনসরা যাওয়ার সময় পথে নামল প্রচণ্ড বৃষ্টি। মোটরসাইকেল থামিয়ে রাস্তার ধারে এক স্কুলে অপেক্ষা করলেন অফিসাররা। সেই বৃষ্টিই সেদিন অপারেশনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। তিরিশ-চল্লিশ মিনিট বাদে বৃষ্টি একটু কমতেই রওনা দিলেন তাঁরা। প্রায় ৪ টে নাগাদ এক সঙ্গে আটটা মোটরসাইকেল ঢুকে পড়ল চাঁনসরা গ্রামে। ছোট গ্রাম চাঁনসরা। সব মিলিয়ে ৩০-৩৫টা বাড়ি। বড়ো রাস্তা থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার দূরের এই গ্রাম ভৌগোলিক ভাবেও মাওয়িস্টদের পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল জায়গা ছিল সেই সময়। কিন্তু সেদিন দুপুরে গোলমাল করে দিল প্রচণ্ড বৃষ্টি। চাঁনসরা গ্রামে মাওবাদীদের প্রভাব ছিল যথেষ্টই। গ্রামের অনেকেরই বাড়িতে আগেও আশ্রয় নিয়েছেন শশধর সহ একাধিক নেতা। তাঁরা যে জঙ্গলের মধ্যে বিভিন্ন গ্রামে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে রাত কাটাতেন, তার মধ্যে একটা ছিল চাঁনসরা। আগের রাতেই সেখানে পৌঁছেছিলেন শশধর, তাঁর স্ত্রী সুচিত্রা এবং আরও তিন-চারজন। গ্রামে ঢোকার মুখেই ছিলেন সেন্ট্রি, গ্রামেরও দু’একজন অন্যান্যবারের মতোই দায়িত্বে ছিলেন, সন্দেহজনক কিছু দেখলেই তাঁদের সতর্ক করার জন্য। কিন্তু সেদিন দুপুরে এক ঘণ্টার প্রবল বৃষ্টি সব গোলমাল করে দিল। সেন্ট্রি থেকে পাহারার দায়িত্বে থাকা গ্রামবাসী, সকলেই একটু ছন্নছাড়া হয়ে যান। প্রবল বৃষ্টির জন্য ঘরে ছিলেন তাঁরা। হয়তো ভাবতে পারেননি, এই বৃষ্টিতে দুপুরে পুলিশ চলে আসতে পারে! কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই এক সঙ্গে আটটা মোটরসাইকেল গিয়ে থামল চাঁনসরা গ্রামে। গ্রামের রাস্তা-মাঠ তখন অলমোস্ট ফাঁকা। গ্রামের এক বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন শশধর, সুচিত্রা এবং আরও তিন-চারজন। এতগুলো মোটর সাইকেলের আওয়াজে চমকে উঠলেন তাঁরা। বুঝে গেলেন পুলিশ এসে গেছে তাঁদের খোঁজে। গ্রামের অল্প কিছু লোক বাইরে ছিলেন, হাতে রাইফেল, সাধারণ প্যান্ট, টি-শার্ট পরা পনেরো-ষোলজনকে হুড়মুড় করে মোটরসাইকেল থেকে নামতে দেখে ভয়েই ঢুকে গেলেন ঘরে। চরম কিছু একটা ঘটবে, এই আশঙ্কায় ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলেন। বুঝলেন, একটা হেস্তনেস্ত হবে আজ। এদিকে গ্রামে তো ঢুকে পড়েছেন, কিন্তু অফিসাররা নিজেরাও জানেন না, কোথায় বা কোন বাড়িতে আছে স্কোয়াড। গ্রামে ঢুকে কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করলেন ষোলজন। তারপর নিলেন এক পরিচিত কায়দা। যেখানে বোঝা যাচ্ছে না মাওবাদীরা কোথায় আছে, তা জানার জন্য পরিচিত ছক। আসলে আচমকা এনকাউণ্টার জলে নেমে সাঁতার শেখার মতোই, তা বই পড়ে হয় না। সেখানে নিজে বাঁচা এবং অপারেশন সাকসেসফুল করার জন্য কতগুলো তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিতে হয়। কখনও তা কাজে লাগে, কখনও লাগেও না। সেদিন একই সঙ্গে দুটো ঘটনাই ঘটেছিল। কীভাবে? পুলিশ এবং সিআরপিএফের দলটা মোটরসাইকেল থেকে নেমে ভাগ হয়ে ছড়িয়ে পড়ল পাঁচ-ছ’টা দলে। সবাই নিয়ে নিলেন পজিশন। এক একটা দলে দু-তিনজন। তারপর একজন শূন্যে একটা গুলি চালালেন। দেখার জন্য, কোনও জবাব আসে কিনা। এনকাউণ্টারের মানসিক যুদ্ধে এই কৌশল অনেক সময়েই কাজে দেয়। লুকিয়ে থাকা লোক ভাবে, তারা কোথায় আছে তা লোকেট করে ফেলেছে পুলিশ। এটাই যে কোনও লুকিয়ে থাকা মানুষের সাধারণ ইন্সটিঙ্কট বা প্রতিবর্ত ক্রিয়া। পুলিশ অপারেশনে এমন বহুবার হয়, গুলির আওয়াজ শুনে বাঁচার জন্য পালটা গুলি চালিয়ে জবাব দেয় তারা। আর সেই গুলির আওয়াজ শুনেই পুলিশ বুঝে যায়, লুকিয়ে থাকা লোকের নির্দিষ্ট লোকেশন। তাই ঘটল সেদিন বিকেলেও। পুলিশ শূন্যে গুলি চালানোর পর কয়েক সেকেন্ড চুপ। কোথাও কোনও শব্দ নেই। কয়েক সেকেন্ড বাদে পুলিশের আর একটা দলও কিছুটা দূরে পরপর গুলি চালাল শূন্যে। শশধররাও বুঝে গেলেন, ঘেরাও হয়ে গেছেন তাঁরা। পাল্টা গুলিয়ে চালিয়ে পালানোর চেষ্টা করা ছাড়া রাস্তা নেই কোনও। এরপর শুরু হয়ে গেল এনকাউণ্টার। যা স্থায়ী হল সাকুল্যে পাঁচ থেকে সাত মিনিট। তারপর সব চুপচাপ।পালানোর জন্য গুলি চালাতে চালাতে শশধর মাহাতো সহ সবাই বেরিয়ে পড়লেন ঘর থেকে। চার-পাঁচজন আলাদা হয়ে গেলেন, এক একজন পালানোর চেষ্টা করলেন এক একদিকে। এটাও তাঁদের একটা কৌশল, সবার একসঙ্গে না থাকা। সবচেয়ে খারাপ কিছু হলেও সবাই যেন ধরা পড়ে না যান। ছোট্ট গ্রাম চাঁনসরা, পরপর বাড়ি, তারই মাঝে গোয়াল ঘর, সরু রাস্তা, হাঁস-মুরগি, ছাগল-গরু বাঁধা। একটা ছোট মাঠ। গুলির শব্দে কেঁপে উঠল এলাকা। ততক্ষণে বাড়ির আড়ালে পুলিশ, সিআরপিএফের দু-তিনজনের ছোট ছোট দলগুলো সেফ পজিশন নিয়ে নিয়েছে। চারদিক থেকে ফায়ারিং করছে পুলিশ। মাঝখানে পড়ে গেল শশধর, সুচিত্রার ছোট্ট স্কোয়াডটা। গুলি চালাতে চালাতে পালানোর সময় পুলিশ-সিআরপিএফের ছোট্ট একটা দলের নিশানার মধ্যে চলে এলেন শশধর মাহাতো। যদিও দলটা জানতো না, মাঝবয়সী যে লোকটা হাতে এ কে ৪৭ নিয়ে এলোপাথাড়ি গুলি ছুড়তে ছুড়তে দৌড়চ্ছেন তিনিই এই স্কোয়াডের লিডার, লালগড় আন্দোলনে কিষেণজির পর মোস্ট ওয়ান্টেড! এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে চালাতে দৌড়নোর সময় শশধর দেখতেও পেলেন না, তিনি চলে এসেছেন টার্গেটের মধ্যে। নাগাড়ে গুলি চালাচ্ছেন জওয়ানরা। সদ্য বৃষ্টিতে ভেজা মাটির রাস্তা কাদায় থিকথিক করছে। শশধর যখন বুঝলেন টার্গেটের মধ্যে চলে এসেছেন, তখন টার্ন নিতে গিয়ে কাদায় পা পিছলে পড়ে গেলেন তিনি। গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর পড়লেন, না কাদায় পা পিছলে পড়ার মুহূর্তে গুলিবিদ্ধ হলেন, তা কোনওদিনই জানা সম্ভব নয়। কিন্তু প্রায় আধঘণ্টা পর মৃতদেহের সামনে পৌঁছে অফিসাররা ভালো করে দেখেন কাদায় পিছলে পড়ার চিহ্ন। দুটো বাড়ির মাঝখানে মাটির দেওয়ালে হেলান দিয়ে পড়ে আছে শশধর মাহাতোর মৃতদেহ। হাতে এ কে ৪৭। হাতে-পায়ে কাদা আর রক্ত। বুক থেকে শরীরের ওপরের অংশ রক্তে ভেসে যাচ্ছে।এদিকে, শশধর যেখানে জওয়ানদের গুলির মুখোমুখি, ঠিক সেই সময়ই কম-বেশি একশো মিটার দূরে একটা বাড়ির আড়াল দিয়ে দৌড়ে পালাচ্ছিলেন সুচিত্রা মাহাতো। তাঁরও হাতে রাইফেল। এক বাড়ির আড়াল থেকে অন্য বাড়ির আড়ালে যেতে পেরোতে হবে ৫০-৬০ ফুট একটা ফাঁকা জায়গা। সেটা পেরোতে গিয়েই সুচিত্রা মুখোমুখি পড়ে গেলেন বিনপুরের ওসি সুকোমল দাসের। সামনে সাক্ষাৎ মৃত্যু, উদ্যত রিভলভার হাতে পুলিশ অফিসার, এক সেকেন্ডের জন্য থমকালেন সুচিত্রা মাহাতো। হাতের রাইফেল তাক করারও সময় পেলেন না। আর একশো হাতের মধ্যে রাইফেল হাতে সুচিত্রাকে দেখে যেন মুহূর্তের মধ্যে বিদ্যুৎ খেলে গেল বিনপুর থানার ওসি সুকোমল দাসের স্নায়ু বেয়ে। এক সেকেন্ডেরও কম সময়ে রিভলভার তাক করলেন সুকোমল দাস। ট্রিগার টিপলেন, খট করে একটা আওয়াজ হল মাত্র। গুলি বেরোল না, লক হয়ে গেল বন্দুক। এমন বন্দুক লক হয়ে যাওয়া একদম অস্বাভাবিক নয়, এক হাজারবারে কয়েকবার হয় হয়তো। হল তো হল, সুচিত্রাকে নাগালের মধ্যে পেয়েই হল তা। যতক্ষণে সুকোমল দাস বুঝলেন গুলি বেরোয়নি, ততক্ষণে সুচিত্রা ৫০ ফুট রাস্তাটা পেরিয়ে চলে গিয়েছেন অন্য বাড়ির আড়ালে। আশ্চর্য নার্ভের জোর সুচিত্রা মাহাতোর। নিশ্চিত মৃত্যুকে সামনে থেকে দেখেও থামেননি এক সেকেন্ডও! নিজেও হয়তো বুঝেছেন, তাঁকে তাক করে থাকা বন্দুক লক করে গেছে, কিন্তু সেটা তো এক সেকেন্ডের কয়েক ভাগ মাত্র সময়, দৌড় থামালেন না তিনি। এই বাড়ি, সেই বাড়ির ফাঁক দিয়ে জল-কাদা পেরিয়ে পালিয়ে গেলেন এ কে ৪৭ হাতে সুচিত্রা মাহাতো। যতক্ষণে সেকেন্ড ফায়ার করতে যাবেন সুকোমল দাস, ততক্ষণে চোখের আড়ালে বাইরে চলে গেছেন সুচিত্রা। বেশি দূর যেতে পারেননি নিশ্চিত, তাড়া করলেন বিনপুর থানার ওসি। কিন্তু এর নাম এনকাউন্টার! রিয়েল লাইফ গুলির লড়াই, এখানে কোনও অ্যাকশন রিপ্লে নেই। কোনও স্ক্রিপ্ট নেই। এখানে প্রতিপক্ষের হাতেও এ কে ৪৭। জীবন নেওয়া এবং জীবন যাওয়া দুইই নির্ভর করে কিছু চান্স ফ্যাক্টরের ওপর। তখনও জল জমে গ্রামের অনেক জায়গায়। দৌড়তে গিয়ে কাদায় পা পিছলে মাটিতে পড়ে গেলেন সুকোমল দাস। লালগড় থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে রামগড়ের গ্রামে ঝড়ে-জলে মাঠে দৌড়ে, গাছে চড়ে বড় হওয়া সুচিত্রা ওই কাদা মাটিতে দৌড়ে গ্রামের এই রাস্তা, সেই রাস্তা পেরিয়ে বেরিয়ে গেলেন পুলিশের নাগালের বাইরে। মাটি থেকে উঠে ফের গুলি চালিয়েছিলেন বিনপুর থানার ওসি, কিন্তু ততক্ষণে সুচিত্রা নাগালের বাইরে। পুলিশ, সিআরপিএফের গুলি এড়িয়ে পালিয়ে গেলেন শশধরের বাকি বাকি সঙ্গীরাও। সব মিলে পাঁচ থেকে সাত মিনিটের অপারেশন। থেমে গেল গুলির আওয়াজ। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ১৬ জন পুলিশ এবং সিআরপিএফ অফিসার-জওয়ান নিজের নিজের জায়গায় অপেক্ষা করলেন মিনিট পনেরো। গ্রামে কোনও কিছুর কোনও শব্দ নেই, ভয়ে গ্রামের গরু, মুরগিগুলোও নিঃশব্দ। গ্রামের সব লোক বাড়ির ভেতরে বন্দি। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই কয়েকশো রাউন্ড ফায়ারিংয়ের শব্দের ঘোর তখনও কাটেনি। দিনের আলো তখনও পরিষ্কার, একে একে অফিসার ও জওয়ানরা জড়ো হলেন এক জায়গায়। অপেক্ষা করলেন কয়েক মিনিট। বুঝতে পারলেন, আর নেই কেউ। দেখলেন, একটা বাড়ির আড়ালে মাটিতে কাত হয়ে পড়ে আছেন মৃত শশধর মাহাতো। হাতের বন্দুক শক্ত করে ধরা। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, পা পিছলে পড়ে গিয়েছেন শীর্ষ মাওবাদী নেতা। শরীরের ওপরের অংশ রক্তে ভেসে যাচ্ছে। বুকে, গলায় গুলির ক্ষত। যদিও তিনিই যে শশধর মাহাতো তা সেই সময় নির্দিষ্ট ভাবে বোঝার কোনও উপায় ছিল না। তবে অফিসাররা আন্দাজ করেছিলেন। পরে এক সোর্সকে ডাকিয়ে এনে তাঁকে মৃত ব্যক্তিকে দেখিয়ে পুলিশ কনফার্ম হয়, লালগড়ের আন্দোলন শুরু হওয়ার পর থেকে তখনও পর্যন্ত সবচেয়ে বড় অপারেশন সাকসেসফুল। সেদিন শশধরের পকেটে পাওয়া গিয়েছিল মোবাইল ফোন, কিছু সিম কার্ড। যে বাড়িতে শশধররা আশ্রয় নিয়েছিলেন, সেখানে পরে সার্চ করে মিলেছিল আরও কিছু বন্দুক। মিলেছিল ব্যাগ, তাতে ছিল শশধর মাহাতোর ওষুধ। জঙ্গলমহলে কাজ করা সমস্ত পুলিশ অফিসার থেকে রাজনৈতিক নেতা কিংবা সাংবাদিক জানতেন, কোনও সাধারণ স্কোয়াড মেম্বার ছিলেন না শশধর মাহাতো। তিনি ছিলেন জেনুইন লিডার এবং কিষেণজির পরেই মোস্ট ওয়ান্টেড নেতা। সিদু সোরেন বা আরও অনেকের মতো লালগড় আন্দোলন শুরু হওয়ার পর হাতে বন্দুক নিয়ে মানুষকে স্রেফ ভয় দেখিয়ে নেতা হননি শশধর মাহাতো। সমস্ত বড়ো অ্যাকশনে নেতৃত্ব দিতেন শশধর। যদিও কয়েক মাস বাদে কিষেণজির যখন পুলিশের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে মৃত্যু হয়, তখন যে প্রশ্ন উঠেছিল এবং এখনও যে প্রশ্ন মাঝে-মাঝেই উত্থাপন করেন অনেকে, একই প্রশ্ন কিন্তু সেভাবে ওঠেনি শশধর মাহাতোর এনকাউন্টারের পরও। কী সেই প্রশ্ন? কীভাবে এনকাউন্টারে একা কিষেণজির মৃত্যু হল, অথচ সুচিত্রা বেঁচে গেলেন? এই প্রশ্ন তো আট মাস আগে চাঁনসরার গ্রামে ওঠেনি সেভাবে! আমার মতে এর কারণ মূলত দুটো।প্রথম কারণ, শশধরের এনকাউণ্টার হয়েছিল সিপিআইএম জমানায়। আর কিষেণজির ক্ষেত্রে তা ঘটেছিল রাজ্যে সরকার বদলের পর তৃণমূল আমলে। যে সিপিআইএম মাসের পর মাস বলে এসেছে, মাওবাদী আর তৃণমূল সব এক, তাদের পক্ষে তো আর নিজের সরকারের আমলে পুলিশের এনকাউণ্টারের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা সম্ভব ছিল না! সেই কারণেই আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের রাজনৈতিক এবং কৌশলগত লাইন সিদু সোরেন, শশধর মাহাতো বা উমাকান্ত মাহাতোর এনকাউণ্টারকে ছাড়পত্র বা প্রকৃত গুলির লড়াইয়ের মর্যাদা দেয়, আর তৃণমূল জমানায় কিষেণজির এনকাউণ্টারে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। আর এই প্রশ্নের মধ্যে একজন মহিলার নাম যুক্ত করতে পারলে যে তা নিয়ে চর্চা এবং রহস্য দুইই বৃদ্ধি পায়, তা চৌত্রিশ বছর সরকার চালিয়ে তো না বোঝার কিছু নেই। এত বছর সরকার চালাতে হলে সাধারণ মানুষের মনস্তত্ত্ব তো খানিকটা বুঝতেই হয়! আর এটাই আমার মতে দ্বিতীয় কারণ। আমাদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজ সেই ২০১১ সালের ১০ মার্চ চাঁনসরা গ্রামের এনকাউণ্টারের পর প্রশ্ন তোলেনি, শশধর মাহাতোর অন্য পুরুষ সঙ্গীরা কীভাবে বেঁচে পালিয়েছিলেন! প্রশ্ন তোলেনি, শশধর মাহাতোর সেন্ট্রিরা কী করছিলেন পুলিশই অভিযানের মুহূর্তে! ঠিক সেভাবেই সে বছরের নভেম্বর মাসেও কেউ প্রশ্ন তোলেননি, কীভাবে কিষেণজির সেন্ট্রি মঙ্গল মাহাতো বেঁচে পালিয়েছিলেন এনকাউণ্টারের সময়? প্রশ্ন উঠেছে স্রেফ সুচিত্রা মাহাতোকে নিয়ে! কারণ, সুচিত্রা মাহাতো যে মহিলা! আত্মসমর্পণ করা সুচিত্রা মাহাতো বা জাগরী বাস্কের যে চরিত্র মূল্যায়ন আমাদের সমাজ করে থাকে, তা করে না আত্মসমর্পণ করা পুরুষ মাওবাদী সুমন মাইতি ওরফে সাঁওতা বা জাগরী বাস্কের স্বামী রাজারামের আত্মসমর্পণের ক্ষেত্রে! কিন্তু এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কেন সফট টার্গেট হিসেবে বারবার এনকাউণ্টারের পর স্কোয়াডে থাকা মহিলাদের চরিত্র মূল্যায়নে এত সময় ব্যয় করেছে, তা নিয়ে কিন্তু মাথাব্যথা ছিল না মাওয়িস্ট শীর্ষ নেতৃত্বের। তাঁদের কাছে শশধর এবং কিষেণজি, দুই মৃত্যুই ছিল সমান গুরুত্বপূর্ণ। কেন এনকাউণ্টার হল, কীভাবে হল, কে খবর দিল পুলিশকে, সবই পরে তদন্ত করে দেখে মাওয়িস্ট নেতৃত্ব এবং তাদের অভ্যন্তরীণ তদন্তে দু’বারই ক্লিনচিট পেয়েছেন সুচিত্রা মাহাতো। কেন এবং কীভাবে, সেই প্রসঙ্গে আসব পরে। আপাতত এই কিষেণজি মৃত্যু রহস্যের প্রায় শেষ লগ্নে এসে আলোকপাত করার চেষ্টা করব এক গুরুত্বপূর্ণ এবং মৌলিক রাজনৈতিক প্রশ্নের ওপর। এবং তারপরই আবার ফিরব, সেই ২০১১ সালের নভেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে কিষেণজির এনকাউণ্টারের ঘটনায়। যেখানে বুড়িশোলের জঙ্গলে সন্ধ্যায় গাছে ফেরা হাজার-হাজার পাখিরও নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গিয়েছিল লাগাতার গুলির শব্দে! ঠিক কী ঘটেছিল সেই সন্ধ্যায়, সেই ঘটনায় ফিরব আবার, যেখান থেকে শুরু হয়েছিল এই লেখা। বিপুল ধৈর্য নিয়ে যাঁরা সাধারণ এক সাংবাদিকের লেখা এই কিষেণজি মৃত্যু রহস্য এতটা বরদাস্ত করেছেন, তাঁরা এতদিনে নিশ্চিতভাবেই জেনে গিয়েছেন এই লেখার উদ্দেশ্য। এই লেখার উদ্দেশ্য সাংবাদিক হিসেবে বারেবারে জঙ্গলমহলে গিয়ে যে সব প্রশ্নের জবাব মেলেনি তা খোঁজা নেওয়া কিংবা যে প্রশ্নের জবাব খোঁজার মতো সময় চব্বিশ ঘণ্টার চ্যানেলে প্রতিদিনকার সাংবাদিকতা অনুমোদন করে না, তার হদিশ করা।যে প্রশ্ন বারবার মাথায় এসেছে, কী কারণে এবং কোন প্রেক্ষাপটে মাওয়িস্টরা এরাজ্যে এতটা শক্তি অর্জন করেছিল? লালগড় আন্দোলনকে কি সত্যিই শ্রেণি সংগ্রাম বলা যায়? সেই সময় এই আন্দোলন নিয়ে যে বহুল প্রচার হয়েছিল দেশজুড়ে, তা কি মাওয়িস্টদের মূল রাজনৈতিক লাইনের প্রসারে কোনওভাবে সহায়ক হয়েছে? এবং শেষমেশ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, এই আন্দোলনই কি রাজ্যে প্রথমে এমসিসি-জনযুদ্ধ এবং পরে মাওয়িস্টদের বিশ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমে যে প্রভাব বিস্তার, তার কোনও উপকার করেছে না ক্ষতি করেছে? এই শেষ প্রশ্নটাই আমার মাথায় বারবার ধাক্কা দেয় ২০১০ সাল থেকে ২০১১ র নভেম্বরের শেষে কিষেণজির এনকাউণ্টার পর্যন্ত। এই সমস্ত প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গিয়ে মনে হয়েছে সাধারণ মানুষ থেকে পিসিপিএ নেতা, এমনকী স্কোয়াড মেম্বার পর্যন্ত কেন বারবার পুলিশকে ফোন করে মাওয়িস্ট নেতাদের ধরিয়ে দিচ্ছিলেন, সেই প্রশ্নের মধ্যেই লুকিয়ে আছে কিষেণজির মতো পলিটব্যুরো সদস্যের মৃত্যু রহস্য। ক্রমশ।..তোমার বাস কোথা যে...- ১২ - Nirmalya Nag | [ এই কাহিনীর সব চরিত্র কাল্পনিক। জীবিত বা মৃত কোনো ব্যক্তির সাথে কোনও মিল যদি কেউ খুঁজে পান তা সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত এবং কাকতালীয়। ] স্কুল ছুটির বেল পড়ে গেছে মিনিট দশ হল। প্রায় ফাঁকা স্টাফ রুমে বসে আছে বিনীতা। ঘরের একদম শেষ প্রান্তে তার টেবিল, আর তার পাশেই আছে একটা জানালা। পর্দাটা সরে গেছে একটু, আর জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে একটা লাল আর একটা হলুদ রঙের পাখি বসে আছে পাঁচিলের পাশে শাল গাছের ডালে। এই পাখিকে মিনিভেট না কী যেন একটা বলে, জানিয়েছিলেন এক সহকর্মী, পুরো নামটা ভুলে গেছে বিনীতা। লালটা মেল আর হলুদটা ফিমেল। আর কিছুদিন পরে ওই শাল গাছে মাখন রঙের ফুল ফুটবে। তার একটা অদ্ভুত সুগন্ধ আছে। আয়ু শেষ হলে মাটিতে পড়ে থাকবে শাল গাছের ফুল। কোনও এক দিন হয়তো শক্তপোক্ত গাছটাও…“কী দেখছিস? বাড়ি টাড়ি যাবি না?” গায়ত্রীর কথায় চটকা ভাঙে বিনীতার। দেখে রুমাল দিয়ে মুখ আর ঘাড়ের জল মুছতে মুছতে তার টেবিলের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে গায়ত্রী। ছুটির পর প্রতিদিনই ভাল করে চোখমুখ ধুয়ে নেয় সে।“হ্যাঁ, এইবার উঠব,” বলে ব্যাগ গোছাতে শুরু করে বিনীতা। চারদিকটা দেখে নেয় গায়ত্রী, পুরো স্টাফরুম এখন ফাঁকা। তারপর বলে, “জানি আমার পক্ষে বলা খুব সোজা, তবু বলব মনটা অন্যদিকে ঘোরানোর চেষ্টা কর। কিছু একটা কাজ খুঁজে বার কর যেটা তোর মনকে অন্যদিকে নিয়ে যাবে… কিছুক্ষণের জন্য হলেও।”একটু হাসল বিনীতা, টেবিলের ওপর কলমটা খুঁজতে খুঁজতে বলল, “রঞ্জিতজি তো এখন দুই বিবি নিয়ে ব্যস্ত।”“আর বলিস না... নতুন দোকান, তার হাজার কাজ। এখন মালপত্র গোছানো চলছে। চালু হয়ে কিছুদিন গেলে আস্তে আস্তে নরমাল হবে। দাদার কী খবর?”“ওই একই রকম। কাজ করে চলেছে। শরীরের দিকে দেখছেই না।” কলমটা পেয়ে গেছে বিনীতা, বলল, “চল।”গায়ত্রী নিজের টেবিল থেকে ব্যাগ তুলে নিল। দু’জনে এগোল দরজার দিকে।আবার বাড়ি, আবার সেই একলা বসে থাকা। আর একলা থাকলেই হাজার রকম চিন্তা পেয়ে বসে বিনীতাকে। স্কুলে যেটুকু থাকা সেইটুকু সময়ই বরং ডাইভারটেড থাকা যায়। অন্য কিছু আর কী করবে সে? বাগান করার দিকে আর একটু মন দেবে? দেখা যাক। কাল শনিবার পুরো দিনটা তো বাড়িতেই থাকবে। বাড়ি ফিরে মালিকে ফোন করল সে। যদিও শনিবার তার আসার দিন নয়, তবু যদি পারে। মালি বলল চেষ্টা করবে, তবে বেলা হবে অনেক। বরং রবিবার সকালে তার আসার সুবিধে আছে। তাতেও অবশ্য অসুবিধে নেই বিনীতার। রান্নাঘরে কিছুটা সময় দিল সে। ধোকার ডালনা বানালো অনেক দিন পরে। ঠিক করল ইউটিউবে নতুন নতুন রেসিপি দেখবে, রঙিনের স্কুলের টিফিনও দেখতে হবে। তারপর বিসপাতিয়াকে শিখিয়ে দিলেই হবে। রান্নায় বিসপাতিয়ার উৎসাহ আছে খুব, নতুন রান্না শিখে নিতে সময় লাগে না। তারপর কিছু ইম্প্রোভাইজ করে, তখন দেখা যায় রান্নার স্বাদ আরও ভাল হয়েছে। রবিবার সকালে মালি এলে তার সঙ্গে একটু আলোচনা করল বিনীতা। বাগানটা একটু অন্যভাবে সাজাতে চায় সে। শীতকালে বাইরে টেবিল পেতে চা খাওয়া যাবে এমন একটা ব্যাবস্থা করার কথা ভাবছে। সেই জায়গাটা বাছতে হবে অবশ্য বিনীতাকেই। বাকি অংশটাও পুরো অন্যরকম করে তুলবে সে। বিনীতা জানে এ সব ব্যাপারে অরুণাভর কোনও আগ্রহ নেই; বাগানে সুন্দর ফুলই ফুটুক আর সেখানে জঙ্গলই হয়ে থাক - দুয়ের মধ্যে কোনও পার্থক্য দেখে না সে।অফিস থেকে সেদিন বিকেলে তুলনায় তাড়াতাড়ি বাড়ি এল অরুণাভ। উইক এন্ডেও কাজ করছে সে। এক এক শনি আর রবিবারে এক এক দফতরের লোকদের নিয়ে বসছে। তবে তাড়াতাড়ি ছেড়েও দিচ্ছে তাদের, তবুও অনেকেই বেশ ক্ষুব্ধ। এত কাজের চাপ আগে আসেনি তাদের কেরিয়ারে - বিশেষ করে সামসের আনোয়ার আর গীতা সিং তো আগে কোনও দিন কাজ করেনি তার প্রোজেক্টে। অরুণাভ ঠিক করেছে এক দিন সবাইকে নিয়ে আউটিং-এ যাবে, চাইলে পরিবারের সদস্যরাও যেতে পারবে। মাঝে মাঝে একটু রিল্যাক্সেশন দরকার সকলেরই। সবাই যে তার মত মেশিন নয় সেটা অরুণাভ বোঝে। সামসেরকে খুব শিগগিরই অস্ট্রেলিয়া যেতে হবে, তার যোগাড়যন্ত্র চলছে। গতবছর একটা কোল কনফারেন্সে ওই দেশে গিয়ে একটা কোম্পানির দু-তিন জন অফিসারের সাথে অরুণাভর ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। শুধু ওই তিন জন নয়, প্রায় সব বিদেশী ডেলিগেটদের সাথেই এই কয় মাস যোগাযোগ রেখে গেছিল সে। এটা তার পুরনো স্বভাব আর সেই কানেকশনই কাজে লাগতে চাইছে এখন। মাঝে মাঝেই ইমেল, হোয়াটসঅ্যাপ বা ফোনেও যোগাযোগ হচ্ছে। সামসেরের ওখান থেকে ফিরে আসতে দশ দিন মত লাগবে। তারপর এই আউটিংটা করা যেতে পারে। আপাততঃ তোপচাঁচি লেকে যাবে বলে ঠিক করে রেখেছে অরুণাভ। দেখা যাক। নিজেই গাড়ি চালিয়ে সবাইকে নিয়ে সেক্টর ফোরে এল অরুণাভ। লোকেশন জানিয়ে দিয়েছিল রঞ্জিত। সিটি সেন্টার আর বোকারো ক্লাবের মাঝামাঝি একটা জায়গায় টেগোর ফ্যাশন হাউস। রবিবার বলে রাস্তায় খুব একটা ভিড় নেই। পার্কিং পেতেও অসুবিধে হল না। দোকানে ঢুকে দেখল খুব আধুনিক ভাবে সাজানো হয়েছে। দোকান বেশ বড়, শপিং মলের বড় বড় দোকানগুলো যেভাবে সাজায় খানিকটা সেই ধাঁচে - তবে ছোট আকারে। বেশ কয়েক জন কর্মচারী রয়েছে, তাদের মধ্যে একজনকে চিনতে পারল বিনীতা। ইনি রঞ্জিতের অন্য দোকান কুসুম ক্লথ স্টোরে ছিলেন।ওদের দেখতে পেয়ে রঞ্জিত আর গায়ত্রী আপ্যায়ন করে ভেতরে নিয়ে গেল। দোকান ঘুরিয়ে দেখাল। রঞ্জিত আলাপ করিয়ে দিল তার পার্টনারের সাথে। আজ মূলত এদের চেনাজানা লোকেরাই এসেছে নিমন্ত্রন পেয়ে।এক ফাঁকে কফি খেতে খেতে রঞ্জিতকে বলল অরুণাভ, “চমৎকার দোকান সাজিয়েছেন তো। খুব ভাল।”“কম্পারেটিভলি কম দামে সিটি সেন্টারের ফিল দিতে চাইছি কাস্টমারদের। তবে দোকান সাজালেই তো হবে না স্যারজী। দোকানের ভাল পাবলিসিটি লাগবে। সে ব্যাবস্থাও করা হয়েছে।”“হ্যাঁ, সে তো করতেই হবে,” বলল অরুণাভ।“হয় ভাল কিছু হবে, নইলে ডুবে যাব। তখন অন্য বৌ আমায় দেখবে আশা করি,” হেসে বলল রঞ্জিত।বিনীতা আর রঙিনকে দেখা যাচ্ছে একটা কাউন্টারে। অরুণাভর কথায় রঞ্জিত তাকে নিয়ে চলল অন্য একটা কাউন্টারের দিকে। শেষে দেখা গেল অরুণাভ বিনীতার জন্য একটা লাল-কালো সিল্ক শাড়ি কিনেছে আর রঙিনের জন্য একটা সাদা ফ্রক কিনেছে আর বিনীতা কিনেছে অরুণাভর জন্য একটা আকাশী নীল রঙের শার্ট আর রঙিনের জন্য একটা জামা-প্যান্টের সেট। কেনাকাটা শেষ করে বাইরে এল সকলে। প্রায় আটটা বাজে। স্ট্রিট লাইটের আলোয় ঝলমল করছে শহর। এই সময়ে বোকারোতে অনেক দিন আসেনি দু’জনের কেউই। রবিবার বলে রাস্তায় গাড়ির ভিড় নেই। ফুটপাথেও লোক কম। সিটি সেন্টারের দিকে গেলে অবশ্য ভিড় বাড়বে।অরুণাভ বলল, “একটু কফি খেলে হয়, কাছেই একটা কাফে আছে।”বিনীতা বেশ অবাক হল। তার স্বামী কাজ ফেলে দোকানে এসেছে সেটাই অনেক অনেক। কেনাটেনা শেষ হলে আবার কফি খেতে চাইছে! হালকা একটু খিদে অবশ্য পেয়েছে।“গাড়ি নিয়ে যেতে হবে?” জিজ্ঞাসা করল বিনীতা।“নাহ। গাড়ি এখানে থাক। হেঁটেই যাওয়া যাবে। বরং ওখানে পার্কিং পেতে সমস্যা হতে পারে।” জামাকাপড়ের প্যাকেট গাড়িতে রেখে হাঁটতে শুরু করল সবাই।“বুঝলি রঙিন, তোর বাবা এর আগে মাত্র একবারই আমার জন্য শাড়ি কিনেছিল,” আড়চোখে বরের দিকে তাকিয়ে বলল বিনীতা।“মাত্র এক বার! না না। বেশি হবে,” বলল অরুণাভ।“নিজে থেকে কিনেছ একবারই। ফার্স্ট অ্যানিভার্সারিতে,” জবাব দিল বিনীতা।দুজনের মাঝখান থেকে রঙিনের প্রশ্ন ভেসে এলঃ “অ্যানিভার্সারি কী?”“অ্যানিভার্সারি হল… অ্যানিভার্সারি হল… আমার আর তোমার মা’র যেদিন দেখা হল, সেই দিনটা,” বোঝাবার চেষ্টা করল অরুণাভ। তারপরেই বলল, “ওই যে কাফে এসে গেছে।” কাফেতে যাওয়ার জন্য রাস্তা পেরিয়ে অন্যদিকে যেতে হল ওদের। টেবিলও পেয়ে গেল। বিনীতা দেখল একটা উঁচু টুলে বসে গিটার বাজিয়ে মাইক্রোফোনের সামনে গান করছে একটা লম্বা চুলওয়ালা ছেলে। সুন্দর গাইছে অরিজিত সিং-এর গাওয়া ‘হামারি আধুরি কাহানি…’। টুলের ওপাশে একটা বুক শেলফ। এখান থেকে অবশ্য কী বই আছে বোঝা যাচ্ছে না। ওয়েটার এলে অরুণাভ অর্ডার দিল তাদের দুজনের জন্য এক প্লেট চিকেন স্যান্ডুইচ আর কাপুচিনো, রঙিনের জন্য একটা চকলেট পেস্ট্রি আর ভ্যানিলা আইসক্রিম। বিনীতা আশা করেছিল অরুণাভ তাকে কী খাবে জিজ্ঞাসা করবে। একটা নিঃশ্বাস ফেলল সে। গায়ক ছেলেটা ইতিমধ্যে একটা ইংরেজি গান ধরেছে, আর অনেকেই হাততালি দিয়ে তাল দিচ্ছে। বিনীতা বুঝল নিশ্চয় জনপ্রিয় গান, তবে তার জানা নেই। “বিলিভার” আর “পেইন” এই দুটো শব্দ ঘুরে ঘুরে আসছিল গানটায়। ইংরেজি গানে অবশ্য তার আগ্রহ নেই। যাতে আগ্রহ আছে সেই রবীন্দ্র সঙ্গীত নিশ্চয় এই ছেলেটা গাইবে না। সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে বিনীতা দেখল অদ্ভুত ডিজাইন - অনেকটা রেডিও বা টিভির সার্কিট বোর্ডের মত। কম্পিউটারের মাদার বোর্ডও নাকি এই রকমই দেখতে হয়। ট্রে-তে করে কফি নিয়ে একজন ওয়েটার আসছে। বিনীতা ব্যাগ সরিয়ে একটু জায়গা করল। কিন্তু না, কফি এল পাশের টেবিলে। ধুত্তোর, কখন আসবে তাদেরটা নিয়ে। রঙিন এমন জায়গায় কখনও আসেনি, অবশ্য বিনীতাও আসেনি। কফিশপ বা কাফে ব্যাপারটা শুধু শুনেছে সে। অরুণাভ কখনও নিয়ে আসেনি। চারদিকে দেখছিল সে, বুকশেলফের পাশে এখন কিশোর কুমারের গান হচ্ছে, “জিন্দগী কে সফর মে…”। অরুণাভ কাউকে ফোন করে পরের দিনের কাজের ব্যাপারে কিছু নির্দেশ দিল। বিনীতা দেখল রঙিন হাই তুলছে। ঘুম পেয়ে গেছে নাকি মেয়ের? হঠাৎই তার নজরে এল অরুণাভর চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে এল কিছু একটা দেখে। তার দৃষ্টি যেদিকে, সেদিকে তাকিয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেল বিনীতা।কাফের দরজা ঠেলে ঢুকেছে ডাক্তার ইন্দ্রনীল বিশ্বাস। (ক্রমশঃ)
জনতার খেরোর খাতা...
হেদুয়ার ধারে - ১৬১ - Anjan Banerjee | রাত একটা বেজে গেল । কাবেরীর কবিতা লেখার নেশা ধরেছে । লিখছে আর কাটছে । যেন অদৃশ্য কার সঙ্গে কাটাকুটি খেলা চলছে কাবেরীর । কেটেকুটে চেঁচে ছুলে যাহোক একটা দাঁড়াল শেষ পর্যন্ত । রাত সওয়া দুটো বাজে । কাবেরীর বেশ ক্লান্ত লাগছে এবার । এই সব ছাই পাঁশ সে কেন যে লিখছে কে জানে । এগুলো কার কি কাজেলাগবে ? অবশ্য দু একজন শ্রোতা বা পাঠক যাই হোক , আছে .... যেমন নীলাঞ্জন , যেমন নিখিল স্যার । ওদের দেখানোর বা শোনানোর জন্যই এই এত রাত পর্যন্ত নিজেকে কষ্ট দেওয়া । এটা একটা নেশার মতো । অমিতাভ, স্নেহাংশুদের নৈর্ঋত-এর কথাও মনে পড়ল । ওখানে সে একটা কবিতা দেবে ঠিক করেছে । ওরা অবশ্য ভীষণ নাক উঁচু । যদি তার কবিতাটা ছাপেভাগ্য ভাল বলতে হবে । ছাপলে এক কপি নিখিল স্যারকে দেবে বলে কাবেরীর খুব ইচ্ছে । নীলাঞ্জনকেও দেবে । ছেলেটা বেশ অন্যরকম । যাকে বলে এক হাতে অসি, আর এক হাতে বাঁশি টাইপের চরিত্র । এই সব ভাবতে ভাবতে কাবেরী একসময় ঘুমিয়ে পড়ল । সন্তোষের উদ্যোগে সাগরের সঙ্গে মোনা মজুমদারের মোলাকাত হল সাগরের বাড়িতেই ।মোনাবাবু বললেন, ' আমার লাইফ রিস্ক থাকলেও আমি আর পলিটিক্স করব না ... 'সাগর বলল, ' তা কেন .... দলে ভাল লোকের সংখ্যাই বেশি । স্বরূপ খাঁড়ার মতো লোকদের দল থেকে সরিয়ে দেওয়া উচিত ... 'মনোরঞ্জনবাবু হেসে বললেন, ' তা হলেই হয়েছে ...'----- ' আমার মতে এরকম একটা লোককে উড়িয়ে দেওয়াই উচিত ... কানুর ব্যাপারটা আমি কিছুতেইভুলতে পারছি না ... ' সাগর বলল ।মনোরঞ্জন এবার গম্ভীর হয়ে গেলেন । বললেন, ' ওড়াতে পারলে তো ভালই হত ... কিন্তু মুশ্কিল আছে ... নাড়াচাড়া হবে খুব ... বরং তলাটাকে আগে ধরলে মনে হয় সুবিধা হবে ...' , মোনা মজুমদার একটা সিগারেট ধরালেন ।----- ' ঠিক আছে ... কিন্তু কানুর দাদা সামনে পড়বে ভাবিনি কখনও । কি আর করা যাবে ...সন্তোষ দিয়েই ডেকে পাঠাই ... ' সাগর বলল ।----- ' কোথায় ডেকে পাঠাবেন ? '----- ' পটলের দোকানে কিংবা আমার বাড়িতে ... '----- ' হ্যাঁ , তা করতে পারেন । যদি চান তো ডাফ স্ট্রিটে আমার ঘরটাতেও ডাকাতে পারেন ... '----- ' হ্যাঁ, সেটাও করা যেতে পারে ... 'তারপর বলল, ' নাঃ .... ভাবছি আমি নিজেই যাব কানুদের বাড়ি । সময় নষ্ট করে লাভ কি ? '----- ' হমম্ ... আচ্ছা , দেখুন তা'লে ... 'বলতে বলতে সৌদামিনী চায়ের কাপ নিয়ে ঘরে ঢুকলেন ।সাগর বলল, ' আমার মা ... 'মনোরঞ্জনবাবু পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন । সৌদামিনীদেবী বললেন, ' বেঁচে থাক বাবা ... 'মনোরঞ্জন অত্যন্ত আন্তরিক গলায় বললেন, ' ভাল থাকবেন মাসিমা । বেঁচে থাকতে তো সবাই চায় .... তবে এই বাঁচাটাই কঠিন হয়ে যাচ্ছে ' , বলে থেমে গেলেন । সৌদামিনীদেবী সাগর মন্ডলের মা । তিনি তার ছেলের অনেক কান্ড দেখেছেন জীবনে । সে সবে তার প্রচ্ছন্ন সমর্থন তো নিশ্চয়ই ছিল । সাগর যথেষ্ট মাতৃভক্ত । কিন্তু সৌদামিনী কখনও সে দুর্বলতার সুযোগ নেননি । মনে মনে উদ্বেগ পোষণ করলেও সাগরের কোন কাজে তিনি কখনও কৈফিয়ত চাননি । সাগরের জীবনে রাত্রি আসার পর তিনি মানসিক দিক দিয়ে অনেক হাল্কা হয়েছেন । তার দৃঢ় বিশ্বাস তার ছেলে কোন অন্যায় করতে পারে না, নাহলে রাত্রির মতো মেয়ে তার সাথী হত না ।সে যাই হোক, এরকম একজন উত্তাল জীবনসমুদ্রের পোড় খাওয়া মাঝি সাধারণ কোন মহিলার মতো কথা বলবেন না , এটাই স্বাভাবিক। তিনি এইসময়ে একটা দামী কথা বললেন । তিনি বললেন, ' ক্ষমার চেয়ে বড় ধর্ম আর কিছু নেই । জীবন নেওয়ার থেকে জীবন দেওয়া অনেক বড়কথা ... 'কথাটা যতই চিরন্তন এবং মহার্ঘ্য হোক , এই পরিস্থিতিতে তা সাগর এবং মনোরঞ্জন কারো মনেই কোন রেখাপাত করল না । তারা এই মুহুর্তে একদম এক অন্য মানসিক পরিস্থিতিতে অবস্থান করছে । মনোরঞ্জনবাবু দায়সারাভাবে ' হ্যাঁ ... তাই তো ... 'বলে চুপচাপ চা খেতে লাগলেন । সাগর কি একটা দরকারে একবার বাইরে গেল । একটু পরে আবার ফিরে এল ।চা খাওয়া হয়ে গেলে মোনা মজুমদার বলল, ' ঠিক আছে আমি তা'লে এখন উঠি । জানাবেন ... আসি মাসিমা , আবার দেখা হবে ... 'সাগর মনোরঞ্জনের সঙ্গে বাইরে গেল । বলল, ' আমাকে তো আমার কাজ করতেই হবে । আপনি আমার সঙ্গে আসায় খুব উপকার হল । তবে, একটু চিন্তাও আছে আপনাকে নিয়ে ... সাবধানে চলাফেরা করবেন । খাঁড়া কি জেনে গেছে ? '----- ' জানি না ঠিক। আপনাদের সন্তোষ দাশ দুটো ছেলেকে দিয়েছে প্রোটেকশানের জন্য । অসুবিধে হবে না । আমিও তো অনেকদিন লাইনে আছি । দু চারটে লোক আমারও আছে । খাঁড়া অত সহজে সুবিধে করতে পারবে না । চিন্তা করবেন না ... জেনে বুঝেই ঝুঁকি নিয়েছি । আসি এখন ... ' সাগর সকাল আটটার সময় কানুদের বাড়িতে গিয়ে কড়া নাড়ল । কোন সাড়া শব্দ নেই । আবার কড়া নাড়া দিল সাগর । ভিতর থেকে একটা আওয়াজ শোনা গেল --- ' আ.. সছি ... ' ।আরও মিনিট খানেক অপেক্ষা করার পর ভিতর থেকে দরজা খুলে গেল । সাগর দেখল একজন রোগামতো শ্যামবর্ণা মহিলা দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছেন । ভীত চকিত চোখের দৃষ্টি । সাগরকে দেখে তাড়াতাড়ি সারা শরীরে ভাল করে কাপড় জড়িয়ে নিলেন । কোন কথা না বলে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সাগরের দিকে তাকিয়ে রইলেন । চোখে মুখে উদ্বেগের চিহ্ন ।সাগর নিরস গলায় বলল, ' প্রীতিময়কে একটু ডেকে দিন না ... ' ভদ্রমহিলা নীচু গলায় বিনীত ভঙ্গীতে বললেন, ' ও তো নেই ... '----- ' নেই ? এত সকালে কোথায় গেল ? '---- ' কাল থেকে নেই ... দেশের বাড়িতে গেছে ... '----- ' দেশের বাড়ি কোথায় ? '----- ' বীরভূমে ... সাঁইথিয়ায় ... '----- ' কবে ফিরবে ? '----- ' বলে যায়নি । দু একদিনের মধ্যেই ফিরবে মনে হয় ... আমি দুই ছেলেমেয়েকে নিয়ে একা আছি ... ' ভদ্রমহিলা স্বভাববশে শাড়িটা আর একবার ভাল করে গায়ে জড়িয়ে নিলেন । সাগরের চোখে পড়ল শাড়িটার দু জায়গায় ছেঁড়া ।সাগর একটু সময় নিল । এরকম যে হতে পারে তার হিসেবের মধ্যেই ছিল । তাই সকাল সকাল এসেছিল । কিন্তু লাভ হল না । সে অন্যদিকে তাকিয়ে কি ভাবতে লাগল ।ভদ্রমহিলা দরজার একটা পাল্লা ধরে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন সাগরের দিকে বিড়ম্বিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে ।বললেন, ' ফিরে এলে কি দেখা করতে বলব ? আগে তো দুদিন দেখা করে এসেছে ... '----- ' কোথায় ? '----- ' আপনি থানা থেকে আসছেন তো ? '----- ' ও ... না না ... আমি পুলিশের লোক না । ওরা কি বারবার ডাকছে ? 'সাগর থানার লোক না শুনে ভদ্রমহিলা বোধহয় কিছুটা স্বস্তি পেলেন ।----- ' তিনদিন ডেকেছে ... থানার থেকে ডাকলেই ওভীষণ ভয় পায় ... আমরা কি জানি বলুন তো ... কানু তো ছোটবেলা থেকে আমাদের সঙ্গে আছে ... ও সাগর মন্ডলের দলে গিয়ে ভিড়ল । আমরা কি বলেছিলাম ভিড়তে ... ওখানে গিয়েই তো যত সর্বনাশ ... এভাবে কি সমাজসেবা করা যায় বলুন ? 'সাগর চুপ করে শুনতে লাগল । এই সময় একটা এগারো বারো বছরের রোগা মেয়ে বেরিয়ে এসে বলল, ' মা , ক্ষিধে পাচ্ছে ... কি খাব ? 'মেয়ের মা বিরক্ত স্বরে বলল, ' রাত পোয়াতে না পোয়াতে পেটের জ্বালা ধরে গেল ! দেখ গিয়ে কৌটোয় মুড়ি আছে কিনা । থাকলে ভাইকে একমুঠ দে ,তুই একমুঠ খে গে যা । আর কিছু নেই এখন ... কি যে পিন্ডির রান্না হবে কে জানে ... বাঁচতে আর ইচ্ছে করে না । কানুকে না মেরে আমাকে তো মারতে পারত ... ' ভদ্রমহিলা কোনরকমে অশ্রু সংবরণ করলেন । মেয়েটা বিরস এবং কুন্ঠিতমুখে ভিতরে চলে গেল । সাগর অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে রইল ।কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সে তার কথায় ফিরে এল আবার ।----- ' কোন থানা থেকে আপনাদের ডাকছে জানেন কি ? '----- ' ওই তো ... মুচিপাড়া থানা । ওসি একবার বাড়িতে এসেছিল । দেখলেই ভয় লাগে ... '----- ' হ্যাঁ , তা ঠিক । ওগুলোকে দেখলেই ভয় লাগে । আমারও তাই । আমরা ছাপোষা লোক ... এসব কি আমরা পারি ... আসল লোককে গিয়ে ধর না ... মনে হয় শালাদের দিই দু ঘা .... আচ্ছা, ওই ওসিটাকে কোন দিন শক্তিপদর সঙ্গে দেখেছেন ? '----- ' ওরে বাবা ... বলেন কি ... দু ঘা দেবেন ! তা'লে আর রক্ষে আছে ... শেষ করে ছাড়বে ... সর্বনাশ ! কি বললেন ... ওসিকে ? হ্যাঁ দেখেছি তো ... ওই তো প্রথম দিনই , বাইরে দাঁড়িয়ে শক্তিপদর সঙ্গে কি সব কথা বলছিল অনেকক্ষণ ধরে ... ' ----- ' ও আচ্ছা , ঠিক আছে । না না ... আমি সত্যি কি আর মারতে যাচ্ছি ? আমার যদি অত ক্ষমতা থাকত তা'লে তো চিন্তাই ছিল না । মানে, মনের ইচ্ছেটা বললাম আর কি ... 'ভদ্রমহিলা এতক্ষণে খানিকটা ধাতস্থ হয়েছেন ।বললেন, ' সেটাই তো ... সেটাই তো ... ' ----- ' আচ্ছা ... বৌদি আপনি শক্তিপদ বিশ্বাসকে আগে চিনতেন ? '----- ' হ্যাঁ হ্যাঁ ... ভালরকম চিনতাম । এ পাড়ায় কে না চেনে ? হাড়বজ্জাত লোক । ওর পাল্লায় পড়েই তো ওর এই দশা হল ... '----- ' কিরকম ? অবশ্য বলতে না চাইলে বলবেন না ... প্রীতিময়বাবু আমার দাদার মতো ... দেখা হলে বুঝতে পারতেন ... 'সাগর বুঝতে পারছে ভদ্রমহিলা সংসারের জোয়াল টানতে টানতে অস্থির নিতান্তই সাদাসিধে এক ঘরোয়া মহিলা এবং ক্রমশ সাগরকে একজন নিরাপদ মানুষ মনে করতে শুরু করেছেন ।তিনি বলে উঠলেন, ' না না ... এ আর কি এমন কথা ... না বলার কি আছে ? আসলে , বুঝতেই তো পারছেন , আমাদের অভাবের সংসার ... লোকটাকে কিছু টাকার লোভ দেখিয়ে এটা ওটা করিয়ে নিত ... যেগুলো ন্যায্য কাজ নয় কোন মতেই ... '----- ' যেমন ? ' ----- ' অতটা আমি জানি না । আমাকে তো বলত না সবকিছু , পাছে আমি ভয় পাই । তবে আমি আন্দাজ করতে পারতাম । ওই শক্তিপদবাবু টাকার কুমীর । মাঝেমাঝেই আসত আর দুজনে মিলে বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে কি সব গুজুর গুজুর ফুসুর ফুসুর করত । মোটে পছন্দ করি না লোকটাকে ... '----- ' ও আচ্ছা আচ্ছা.... আর বলতে হবে না , বুঝতে পেরেছি ... '------ ' আচ্ছা বৌদি আপনি স্বরূপ খাঁড়া বলে কারও নাম শুনেছেন ? 'এবারে ভদ্রমহিলা চমকে উঠলেন । সাগর খেয়াল করল তার গলার আওয়াজ একটু কেঁপে গেল ।---- ' স্ব..রূপ ...কি বললেন ? '---- ' খাঁড়া '---- ' ন্না না ... সে আবার কে ? ওসব কাউকে চিনি না ... খাঁড়া টাঁড়া আবার কে ? নামই শুনি নি ... 'সাগর বুঝতে পারল এতক্ষণে সে ঠিক জায়গাটায় টোকা দিতে পেরেছে । এত জোরদার অস্বীকার মোটেই স্বাভাবিক ব্যাপার নয় । এটা অন্য কোন অর্থ বোঝায় ।সে বলল, ' ও আচ্ছা আচ্ছা ... ঠিক আছে ঠিক আছে ... কিছু মনে করলেন না তো ? 'ভদ্রমহিলার নাম রানু । তার কিছু মনে করার যে কোন মূল্য আছে সেটাই রানু ভুলে গেছে বহুকাল আগে । সে অসংলগ্নভাবে বলল, ' না না ... সে কি কথা ... সে কি কথা ... 'সাগর এবার বলল, ' আপনার অনেকটা সময় নষ্ট করে দিলাম ... সকালবেলা আপনাদের কাজকর্মের সময় .... এখন এসব বাজে বকবক করছি ... খুব খারাপ লাগছে । প্রীতিময়দা আমার দাদার মতো , উনি আমার কাছে দু'শ টাকা পেতেন । সেটাই দিতে এসেছিলাম । তা উনি যখন নেই আপনাকেই দিয়ে যাই ... এই নিন ... 'রানু তো আকাশ থেকে পড়ল । তার বর যে কাউকে টাকা ধার দেবার ক্ষমতা রাখে সেটা তার কল্পনারও বাইরে । সে বেশ থতমত খেয়ে গেল বটে তবে টাকাটা হাত বাড়িয়ে নিয়ে নিল । সাধা লক্ষী পায়ে ঠেলতে নেই এই আপ্তবাক্য গরীবের ভুললে চলে না । রানুর মুখে একটা স্বস্তি মাখানো হাসির আভা এসে পড়ল তার নিজের অজান্তেই। সে বলল, ' আপনার নামটা কি বলব ওকে ? '----- ' নাম টাম কিছু বলতে হবে না । এমনিই বুঝতে পারবে ... পরে তো দেখা হবেই। আজ আসি তা'লে ... ও হ্যাঁ ... একটা বলছিলাম ... সাগর মন্ডল তো কানুর এই অবস্থার জন্য অনেকটা দায়ী বলছেন ... '----- ' একটু কি ! ... পুরোপুরি দায়ী .... সামনে পেলে আচ্ছা করে শুনিয়ে দিতাম ... কি আর করবে ? মড়ার ওপর আর ক' ঘাই বা খাঁড়ার ঘা মারবে ? মারে মারুক .... মরতেই তো চাই... '----- ' সেটাই বলছি ... আমি যদি আপনার সামনে সাগরকে হাজির করাতে পারি আপনার সব কথা খুলে বলতে পারবেন তো ? ভয়ের কিছু নেই । আমি সঙ্গে থাকব । সব সামলে নেব ... '----- ' অ্যাঁ , সে কি কথা ! আপনি ওসব করতে যাবেন না । কেন মিছিমিছি নিজের বিপদ ডেকে আনবেন ? সে কি সোজা লোক ? আপনি ওসব পারবেন না ... '------ ' চেষ্টা করে দেখি না ... পেরেও তো যেতে পারি ... আসলাম ... আবার দেখা হবে ... 'সাগর দ্রুতবেগে হাঁটতে লাগল আমহার্স্ট স্ট্রিটের দিকে ।( চলবে )********************************************এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের কাহিনী - অর্ঘ্যদীপ চক্রবর্তী | কোনো এক গ্ৰামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করতেন। নাম তাঁর অনিল চক্রবর্তী। তিনি বিবাহ করেননি।ফলে একাই থাকতেন আর বিভিন্ন লোকের বাড়িতে যদি কোনো পুজো থাকত তাহলে পুজো করতেন, এই পুজো করে যা পেতেন তা দিয়েই কোনোরকমে দিন চালাতেন।খুব সুখে যে তাঁর দিন চলত এমন বলা যায় না আবার খুব দুঃখেও দিন চলত না। একা মানুষ থাকতেন নিজের মতো আর যা আয় হতো তাই দিয়েই কোনোমতে টেনেটুনে দিন কাটিয়ে দিতেন।ব্রাহ্মণ মানুষটি খুব সৎ ছিলেন। সারাদিন ধরে কৃষ্ণ নামে মেতে থাকতেন। নিজে পুজো করে যতটুকু পেতেন তাতেই সন্তুষ্ট থাকতেন। অতিরিক্ত চাহিদা তাঁর মধ্যে ছিল না।একদিন পুজো করে ফিরছেন অনিল চক্রবর্তী। সেদিন তিনি চাল,ডাল, আলু, তেল ভালো পরিমাণে পেয়েছেন একটি বাড়িতে পুজো করে। মনে মনে ভগবানের জায়গান করতে করতে ফিরছেন বাড়ির পথে। হঠাৎ দেখলেন এক জায়গায় পথের পাশে কিছু সোনার গয়না পড়ে আছে। তিনি কাছে গেলেন। একবার এদিক ওদিক তাকালেন। কাউকে দেখতে পেলেন না। ওগুলোর দিকে তাকিয়ে তিনি ভাবলেন, গয়নাগুলো যদি আমি সোনার দোকানে বিক্রি করি তাহলে তো অনেক টাকা পাব। তখন আমার বাড়িতে নূন্যতম অভাবও থাকবে না। পরক্ষণেই আবার ভাবলেন --- নাঃ, এইসব চিনি না জানি না --- কার গয়না --- না নেওয়াই ভালো। তিনি ছুঁয়েও দেখলেন না সেগুলো। তিনি ভাবলেন, আমার যেমন চলছে তেমনই চলুক, ভগবান চাইলে আমার অবস্থা আরও ভালো হবে। অনিলবাবু আরও ভাবলেন --- ছোটোবেলায় তো পড়েছিলাম লোভে পাপ পাপে মৃত্যু। তিনি চলে গেলেন সেখান থেকে।সেদিন রাতে স্বপ্ন দেখলেন। স্বপ্নে দেখলেন পরমপুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বলছেন --- তুমি সত্যিই সৎ। আমি তোমার সততার পরীক্ষা নিচ্ছিলাম। তোমার মধ্যে কোনো লোভ নেই। এটাই আমার ভালো লেগেছে। তুমি শীঘ্রই একটি ভালো সংবাদ পাবে।এরপর বেশ কয়েকদিন কেটে গেল। তিনি একদিন তাঁর প্রতিবেশীর মুখ থেকে জানতে পারলেন যে, তাদের গ্ৰামের জমিদার বাড়িতে যে পুরোহিতটি নিত্য পুজো করত সে মারা গেছে। তাই জমিদার মশাই নতুন কোনো পুরোহিত খুঁজছেন। জমিদারবাবু খুব তাড়াতাড়ি চাইছেন কারণ তাঁর গোপালের নিত্য পুজো বন্ধ হয়ে গেছে। জমিদার বাড়ির পুরোহিতটি তিন চারদিন হলো মারা গেছেন। অর্থাৎ আর সময় নষ্ট করা উচিত হবে না মনে করে সেদিনই অনিলবাবু রওনা হলেন জমিদার বাড়ির উদ্দেশ্যে।এরপর বেশ কয়েকমাস কেটে গেছে। তিনি জমিদার বাড়ির নিত্য পুজোর কাজটি পেয়ে গেছেন। এখন তাঁর ঘরে আর কোনো অভাব নেই। প্রতিদিনই জমিদার মশাই পুজোর শেষে অনেক কিছু দেন তাঁকে।যে সৎ যে নির্লোভ ভগবান তাকে সাহায্য করেন।--- অর্ঘ্যদীপ চক্রবর্তী২৬/৭/২০২৪
ভাট...
 যদুবাবু | নীল এলিয়েন চেনা চেনা লাগছে। উনি সম্ভবতঃ ক্রেনিয়াস গ্রহের বাসিন্দা অ্যাঙ। বাকীদের চিনি না। অবশ্য শিল্পী কাকে ভেবে এঁকেছেন উনিই জানেন। আর ছবিতে রমিতের ছাপ স্পষ্ট। :)
যদুবাবু | নীল এলিয়েন চেনা চেনা লাগছে। উনি সম্ভবতঃ ক্রেনিয়াস গ্রহের বাসিন্দা অ্যাঙ। বাকীদের চিনি না। অবশ্য শিল্পী কাকে ভেবে এঁকেছেন উনিই জানেন। আর ছবিতে রমিতের ছাপ স্পষ্ট। :) &/ | গুরুচন্ডা৯তে পাতার উপরের দিকে ওই আসিতেছে ছবিটাতে একপাশে খাড়াচুল এক যুবক, লালটুপিপরা এক বৃদ্ধ, নীল এলিয়েন--এঁরা কারা? অন্যপাশে তিনকোণামুখ চোখা নাক এক মহিলা, অল্প দাড়িয়ালা এক বিস্মিত হতভম্ব যুবক বুকে ফোন আঁকড়ে আছেন, এঁরাই বা কারা? অন্য লোকজনরাই বা কারা? ছবিটা কার আঁকা?
&/ | গুরুচন্ডা৯তে পাতার উপরের দিকে ওই আসিতেছে ছবিটাতে একপাশে খাড়াচুল এক যুবক, লালটুপিপরা এক বৃদ্ধ, নীল এলিয়েন--এঁরা কারা? অন্যপাশে তিনকোণামুখ চোখা নাক এক মহিলা, অল্প দাড়িয়ালা এক বিস্মিত হতভম্ব যুবক বুকে ফোন আঁকড়ে আছেন, এঁরাই বা কারা? অন্য লোকজনরাই বা কারা? ছবিটা কার আঁকা?
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাকাদামাটির হাফলাইফ - ইট পাথরের জীবন - ইমানুল হক
২৭ জুলাই ২০২৪ | ৩১ বার পঠিতস্বাধীন দেশে রাজা এবং প্রজার ধারণা এক মানসিক দাসত্ববৃত্তি থেকে আসে। তাই সাধারণতন্ত্র না বলে প্রজাতন্ত্র দিবস বলেন কেউ কেউ। । আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে খুব ঘটা করে পালন হতো ২৬ জানুয়ারি ও ১৫ আগস্ট। প্রধানশিক্ষক ছিলেন আমার বড়োমামা। কংগ্রেসের বড়ো নেতা। বোঁদে দেওয়া হতো। পতাকা তোলার পর গোটা গ্রাম মিছিল করে ঘোরা শেষে। মাঝপথে কেউ যাতে না পালায়, তাই শেষে মিষ্টি। আমরা সিপিএম বাড়ির ছেলে। পিছনের দিকে থাকতাম। বন্দে বলে আওয়াজ উঠলেই আলতো করে বলে উঠতো কেউ কেউ, বোঁদে ছাগলের পোঁদে। তবে বোঁদে খাওয়ার সময় এ-সব কারও মনে থাকতো না। আমার মনে পড়ে না জুনিয়র হাইস্কুলে এ-সব পতাকা উত্তোলনের রেওয়াজ ছিল কি না! তবে সেহারা স্কুলে পড়ার সময় বেশ ভিড় হতো। ছাদে। বক্তৃতাও হতো। মিল মালিকের ছেলে কংগ্রেসের অবদান বললে, তেড়ে আধঘন্টা বক্তৃতা করে ধুইয়ে দিয়ে বলেছিলাম, ইয়ে আজাদি আধা হ্যায়। টাটা বিড়লা গোয়েঙ্কারা দেশ লুঠছে। তখন তো আদানি আম্বানিদের দেখি নি। তাহলে কী বলতাম জানি না। তখন বলেছিলাম, মাথাপিছু ৬০০ টাকা ঋণ।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালঔপনিবেশিক হিন্দু আইন : ২ - এলেবেলে
২৬ জুলাই ২০২৪ | ৫৯ বার পঠিত বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাএই বর্ষার কবিতা - সোমনাথ রায়
২৬ জুলাই ২০২৪ | ১৩৫ বার পঠিতসে-কবিতা কেন লিখে যাচ্ছি আজও এতদিন ধরে তাই ভাবি অনর্থক কেন আহ্বান করছি ধারাপাত শব্দ এযাবৎ অথচ অবাক আমি বুঝিইনি আকাশের দাবি সে-বিকেলে রাস্তার আলস্যে ছাউনির নিচে অপেক্ষা করেছে সাইকেল
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালকিষেণজি মৃত্যু রহস্য - পর্ব ১৯ - বিতনু চট্টোপাধ্যায়
২৬ জুলাই ২০২৪ | ১০৩ বার পঠিতএই পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কেন সফট টার্গেট হিসেবে বারবার এনকাউণ্টারের পর স্কোয়াডে থাকা মহিলাদের চরিত্র মূল্যায়নে এত সময় ব্যয় করেছে, তা নিয়ে কিন্তু মাথাব্যথা ছিল না মাওয়িস্ট শীর্ষ নেতৃত্বের। তাঁদের কাছে শশধর এবং কিষেণজি, দুই মৃত্যুই ছিল সমান গুরুত্বপূর্ণ। কেন এনকাউণ্টার হল, কীভাবে হল, কে খবর দিল পুলিশকে, সবই পরে তদন্ত করে দেখে মাওয়িস্ট নেতৃত্ব এবং তাদের অভ্যন্তরীণ তদন্তে দু’বারই ক্লিনচিট পেয়েছেন সুচিত্রা মাহাতো।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালতোমার বাস কোথা যে...- ১২ - Nirmalya Nag
২৫ জুলাই ২০২৪ | ১৯১ বার পঠিতগায়ক ছেলেটা ইতিমধ্যে একটা ইংরেজি গান ধরেছে, আর অনেকেই হাততালি দিয়ে তাল দিচ্ছে। বিনীতা বুঝল নিশ্চয় জনপ্রিয় গান, তবে তার জানা নেই। “বিলিভার” আর “পেইন” এই দুটো শব্দ ঘুরে ঘুরে আসছিল গানটায়। ইংরেজি গানে অবশ্য তার আগ্রহ নেই। যাতে আগ্রহ আছে সেই রবীন্দ্র সঙ্গীত নিশ্চয় এই ছেলেটা গাইবে না।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালবিশ্বভরা প্রাণ - মোহাম্মদ কাজী মামুন
২৫ জুলাই ২০২৪ | ১০৩ বার পঠিতহঠাৎই সভাকক্ষে হাসির মৃদু ঢেউ বয়ে গেল! কিন্তু সেই হাসি থামতে না থামতেই এক কম বয়সী লোক, বোধ করি, সভার তরুণতম আলোচক, উঠে দাঁড়ালেন। মুহূর্তেই সব চোখ তার দিকে ঘুরে গেল। লোকটির চোখে-মুখে খেলে যাচ্ছিল অলৌকিক এক আভা, বিজ্ঞানীরা একে ভাল করেই চেনেন; তাদের ভাষায় এ হচ্ছে ইউরেকা লাইট। আস্তে আস্তে বোমাটা বের করতে শুরু করলেন সেই তরুণ তার শ্মশুমন্ডিত মুখের গোপন দুয়ার থেকে, "একটা চিন্তা এসেছে আমার মাথায়! জানি না আপনাদের কাছে কতটুকু গ্রহণযোগ্য হবে, তবে আমার মনে হচ্ছে, কাজে দেবে। ওদেরকে আবার এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে দিতে হবে আমাদের। আবার আগের মত স্থবির, আনত করে দিতে হবে। “
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালতোমারে বধিবে যে... - বিপ্লব রহমান
২৪ জুলাই ২০২৪ | ১৯২ বার পঠিতএই সহিংসতার শুরু অবশ্য পুলিশ-ছাত্রলীগ সখ্যতায়। রঘু ডাকাতের দল হেলমেট লীগ ঢাকা, জাহাঙ্গীর নগর, রাজশাহীসহ আরো সব বিশ্ববিদ্যালয়ে নারী-পুরুষ শিক্ষার্থীদের নিষ্ঠুর লাঠিপেটায়, প্রকাশ্যে গুলিতে ও ইটপাথরের আঘাতে দমন করতে চায় আন্দোলন স্রোত। যা ক্রমেই সরকারি চাকরির কোটা সংস্কার থেকে সরকার বিরোধী রাজনৈতিক রূপ নিতে থাকে। শ্লোগান উঠে, তুই রাজাকার, তুই রাজাকার! স্বৈরাচার! স্বৈরাচার! .
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালকারফিউ ডাইরি! - sadequzzaman sharif
২৪ জুলাই ২০২৪ | ৬৪৭ বার পঠিতনেট পুরোপুরি বন্ধ আর কারফিউ চালুর পরে দৈনিক রাতে যা জানতাম আর যা বুঝতাম তা লেখার চেষ্টা করে গেছি। সব সময় মাথা ঠিক ভাবে কাজ করেছে এমনও না। পুরোটা আবার বসে বসে পড়লে হয়ত অনেক কিছুই বাদ দিতাম আমি। কিন্তু নেট পেয়েছি, আবার কখন নেটের বাহিরে চলে যাই ঠিক নাই। তাই পুরো লেখাটাই একবারে দিয়ে দিলাম। ইচ্ছা ছিল ভাগ ভাগ করে দেওয়ার। সরকার ফেসবুককে ভয় পাচ্ছে। এইটাই হচ্ছে সত্য। নেট দিতে আমার মনে হয় না আর অন্য কোন সমস্যা আছে। ফেসবুকে মানুষ এতদিন যা হয়েছে তার ভিডিও চিত্র, স্থির চিত্র দেখবে, দেখে আবার যদি রাগের বিস্ফোরণ ঘটে? সরকার তা চাচ্ছে না। সহজ একটা বিষয়কে কতখানি জটিল করা যায় তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ হয়ে থাকবে এই আন্দোলনটা। নতুন প্রজন্মের কাছে জনপ্রিয়তা এখন প্রায় শূন্যের কাছে। অথচ জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারত এখান থেকে। আজকের প্রথম আলোর রিপোর্ট অনুযায়ী মৃত্যুর সংখ্যা ১৯৭! আমার এই লেখায় এক জায়গায় লেখছি ধার্মিকেরা বলে ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন, সেই মহান মঙ্গলের অপেক্ষায় বসে থাকা ছাড়া আর কিছুই করার নাই। এখনই ওইটাই বলছি! অদ্ভুত কালো অধ্যায় পার করল বাংলদেশ।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালউঁচু-নীচু জ্যোৎস্না - যদুবাবু
২৪ জুলাই ২০২৪ | ৩০৭ বার পঠিতভাস্কর লিখেছিলেন ‘শেষ নেই এমন এক পাহাড়ে অনবরত চড়তে থাকার সঙ্গে কবিতা লেখার তুলনা করা যায় কিছুটা’... সেই বোবাপাহাড়ের ঠিক তলায় দাঁড়িয়ে আমি, সিসিফাসের উত্তরাধিকার বহন করে চলেছি যেন, তবু বিশ্বাস করি এরপরের স্টপেই আলো-ভরা উপত্যকা আসছে একটা, আর অনেক চিঠি হাতে সেখানে আমার জন্য নিশ্চয়ই একটা আস্ত ডাকবাক্স বানিয়ে রেখেছেন একজন রুপোলি চুলের নিঃসঙ্গ মানুষ।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালবাড়ি বৃত্তান্ত - শক্তি দত্ত রায়
২৪ জুলাই ২০২৪ | ২৬৭ বার পঠিতকয়েক দিন ধরে মনে হচ্ছে যে বাড়ি গুলোতে জীবনের দিন সব কাটিয়ে এলাম শেষ বেলায় তাদের কথা একটু লিখে যাই। যাই বলছি বটে যাওয়ার নাম গন্ধ নেই। জাঁকিয়ে বসেছি মাটি মায়ের কোল আঁকড়ে। লিখতে অসুবিধা হয়। আস্তে আস্তে লিখবো খণ্ড খণ্ড। সেভ করতে গিয়ে লেখা হারিয়ে ফেলি। অনেকের জীবন এক বাড়িতে কেটে যায়। আমাদের তা হয়নি। ছোটবেলা থেকে কতো বাড়িতে থাকলাম। যেটুকু মনে আছে লিখতে থাকি। সুখে জড়ানো না হোক স্বস্তি শান্তি তো ছিল। মা বাবা ভাইবোন, দুএকজন সহায়ক, গৃহপালিত নিয়ে মধবিত্ত পরিবার। হাসি খুশি মোটামুটি খেয়ে মেখে মন্দ কাটেনি বলতে পারি। যাঁরা পড়বেন জেনে বুঝেই অপ্রয়োজনের আনন্দে পড়বেন।
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাবৈদিক গণিত বিপন্ন? - সুনন্দ পাত্র
২৩ জুলাই ২০২৪ | ২৪২০ বার পঠিতগত ১২ই জুলাই, শুক্রবার, অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে পনেরোতম আন্তর্জাতিক গণিত-শিক্ষণ কংগ্রেস-এর সম্মেলন থেকে অধ্যাপক জয়শ্রী সুব্রহ্মনিয়নকে নিরাপত্তা-আধিকারিকরা প্রহরা দিয়ে বের করে দেন। তাঁর ব্যাজ বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং রেজিস্ট্রেশন প্রত্যাহার করা হয়। কারণ হিসেবে তাঁকে বলা হয়, যে, সেদিন সকাল ন-টায় অধ্যাপক আশিস অরোরা-র বৈদিক গণিতের অধিবেশনে তাঁর করা কিছু মন্তব্যকে কিছু অন্য অংশগ্রহণকারীর শাসানিমূলক ও ভীতিপ্রদ মনে হয়েছে। কতটা আতঙ্কের উদ্রেককারিণী এই ভারতীয় গণিত-অধ্যাপক? কতটা ভয়ঙ্কর তাঁর উপস্থিতি, যার ফলে তাঁকে শিক্ষকদের সম্মেলন থেকে বের করে দিতে হয়? ‘বৈদিক গণিত’ ঠিক কীরকম বিপন্ন হয়েছিল তাঁর উপস্থিতিতে? এসব কথা জানতে, সেই অধিবেশনেরই আরেক শ্রোতা এবং ওই সম্মেলনের আরেক নিমন্ত্রিত বক্তা, ওহায়ো স্টেট ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক থিওডর চাও-এর বয়ান পড়ে ফেলুন।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালবিবিধার্থ সংগ্রহ ওরফে যা ইচ্ছে বিষয়ে হিজিবিজি বকবক - স্বাতী রায়
২২ জুলাই ২০২৪ | ২৮৭ বার পঠিত হরিদাস পাল
হরিদাস পালআক্রমণকারী তৈমুরকে কী চোখে দেখতেন হিন্দুস্থানের মোঘল বাদশাহরা : উপল মুখোপাধ্যায় - upal mukhopadhyay
২১ জুলাই ২০২৪ | ১১৯ বার পঠিত হরিদাস পাল
হরিদাস পালঔপনিবেশিক হিন্দু আইন - এলেবেলে
২০ জুলাই ২০২৪ | ৪০৭ বার পঠিতদেওয়ানি লাভ করার মাত্র ৭ বছরের মধ্যেই ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার নারীদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে একেবারে প্রান্তিক করা ও সমাজকে ক্রমশ পিতৃতান্ত্রিক করে তোলার জন্য বিভাজনমূলক আইন চালু করার উদ্যোগ নেয়। প্রথমে হেস্টিংস ও পরে কর্নওয়ালিসের উদ্যোগে তৈরি হয় ঔপনিবেশিক হিন্দু আইন, যার নিদর্শন প্রাক্-পলাশি বাংলায় ছিল না। ১৯৫৫ সালে হিন্দু কোড বিল পাস না হওয়া পর্যন্ত এই ঔপনিবেশিক আইনটি এ দেশে পুরোদমে বিদ্যমান ছিল। কোন প্রেক্ষাপটে ও কী উদ্দেশ্যে ঔপনিবেশিক শাসকরা এই আইন তৈরি করে, তার সুলুকসন্ধান করাই এই ধারাবাহিক প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য।
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাবিপ্লবের আগুন - পর্ব চোদ্দ - কিশোর ঘোষাল
২০ জুলাই ২০২৪ | ২৯২ বার পঠিত... যে কথা বলছিলাম, রাজধানীর ঘটনাটা যেদিন ঘটেছিল, শুনেছি সেই রাত্রেই ভল্লা রাজধানী থেকে রওনা হয়েছিল। রাজধানী ছাড়ার পর চতুর্থ দিন ভোরে সে আমাদের গ্রামে এসে পৌঁছেছিল পায়ে হেঁটে। বিপর্যস্ত অবস্থায়। রাজধানী থেকে আমাদের গ্রামের যা দুরত্ব, সেটা তিনদিন, তিন রাত পায়ে হেঁটে আসা অসম্ভব। বিশেষ করে ওরকম অসুস্থ অবস্থায়। তার মানে দাঁড়াচ্ছে ও বেশিরভাগ পথটাই এসেছিল হয় ঘোড়ায় চড়ে অথবা রণপায়..
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালযোগীনদাদা এখন - শেখরনাথ মুখোপাধ্যায়
২০ জুলাই ২০২৪ | ৯৬ বার পঠিতআহা, ফিরে আসি হাৎরাসে। এ যোগীনদাদা সে যোগীনদাদা নয়। শোনা যাচ্ছে যোগীরাজ্যের যোগীনদাদা এখনও হাৎরাসে গিয়ে উঠতে পারেননি। এমনকি, একটা এফ-আই-আরও হয়নি সাকারবাবার নামে। ভালোই। রেগেমেগে শেষ পর্যন্ত পৌঁছতেনও যদি দাদা (যোগীন অর্থাৎ যোগীরা বাবাও আবার দাদাও), তাহলে আবার অনত্থ হয়ে যেতে পারত, তাই না? যোগীনদাদা শুনেছি আজকাল বুলডোজার ছাড়া আর কিছু চড়েনই না!
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাক্যালিডোস্কোপে দেখা – ভো-কাট্টা - অমিতাভ চক্রবর্ত্তী
২০ জুলাই ২০২৪ | ৪৬৬ বার পঠিতবাবা বারান্দায় বসে একধাপ নিচের সিঁড়িটায় একটা যুৎসই উচ্চতার কাঠের টুকরো রেখে তার উপর বাঁশের টুকরোটা দাঁড় করিয়ে দা দিয়ে সেটাকে লম্বালম্বি কয়েকটা টুকরোয় চিরে ফেলল। তারপর তাদের একটার গা থেকে দা দিয়ে কয়েকটা ছিলকা বার করে নিয়ে ছুরি দিয়ে সেগুলোকে চেঁছে চেঁছে কয়েকটা মসৃণ এবং নমনীয় কাঠি বানিয়ে নিল। এরপর রঙিন কাগজের বান্ডিল থেকে একটা কাগজকে টেনে নিয়ে সেটাকে ভাঁজ করে, ভাঁজ বরাবর ছুরি টেনে তার থেকে একটা বর্গাকার টুকরো বার করে আনল। এরপর ঐ কাঠিগুলোর একটাকে সেই কাগজের টুকরোটার উপর রেখে কাঠির গোড়া যদি এক নম্বর কোণায় রাখা হয়েছে ধরি, তবে অন্য প্রান্তকে তিন নম্বর কোণার দিক করে বসিয়ে কোণা ছাড়িয়ে দুই কি তিন ইঞ্চি দূরে ছুরি দিয়ে কাঠির গায়ে দাগ কেটে তারপর দাগ বরাবর দু’ টুকরো করে, দাগের প্রান্ত আর গোড়ার প্রান্তকে একটা সুতো দিয়ে আলগা করে বেঁধে একটা ধনুক বানিয়ে ফেলল। সুতোটা তখনো ঢিলা রেখে ধনুকটাকে এবার চৌকো কাগজের উপর বসিয়ে ঠিকমত আকারে এনে সুতোর সেই ছিলা টাইট করে বেঁধে ফেলা হল। ধনুকের দুই মাথা কাগজের এক আর তিন নম্বর কোণা ছুঁয়ে আছে। আমরা ভিতরে ভিতরে উত্তেজনায় ছটফট করলেও শান্তভাবে বসে দেখে যাচ্ছি।
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাচেকিয়া এক - হীরেন সিংহরায়
২০ জুলাই ২০২৪ | ৩৯৫ বার পঠিতআলাপ জমে গেলো ফ্রান্তিসেকের সঙ্গে। টি টুয়েন্টি নামক দানবের দুরাচার শুরু হবার আগে টেস্ট ক্রিকেটের মাঠে গল্প বেশি জমতো - অনেকক্ষণ যাবত মাঠে কিছুই ঘটে না, স্যাকরার ঠুক ঠাক চলে ব্যাটে বলে। ফুটবলের মাঠে সেটা সম্ভব নয়। তবু খেলার আগে, মাঝে, হাফ টাইমে কিছু কথা। আমরা তাঁকে একাধিক বিয়ারে আপ্যায়িত করেছি, কিছুতেই দাম দিতে দেব না! ভারত ও পূর্ব ইউরোপের ভাইচারা যুগ যুগ স্থায়ী হোক। দুজন ভারতীয়ের সঙ্গে এই ফ্রাঙ্কফুর্টের মাঠে দেখা হবে তিনি ভাবতে পারেন নি! আমার ট্রিভিয়া লাইব্রেরির শ্রীবৃদ্ধির জন্য যত না প্রশ্ন, ভারত সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞানস্পৃহা অনেক বেশি। ততক্ষণে তাঁর টিম আইনত্রাখত ফ্রাঙ্কফুর্টের হাতে বেশ ঝাড় খাচ্ছে, ৩-০ গোলে পিছিয়ে এবং তাঁর মনোযোগ বিভ্রান্ত। তাই প্রস্তাব দিলাম- তিনি যদি চান আমরা একত্র হেঁটে শহরে ফিরতে পারি, এক ঘণ্টার পথ। ট্রামে বেজায় ভিড় হবে। ফ্রান্তিসেক বললেন যদি আমরা তাঁকে ট্রেন স্টেশনের কাছাকাছি অবধি সঙ্গ দিতে পারি তাঁর খুব উপকার হয়, রাতের ট্রেন ধরবেন। সেটাই আমাদের লজিস্টিক, ফ্রাঙ্কফুর্ট হাউপটবানহফের সামনে আমরা বারো নম্বর ট্রাম ধরে বাড়ি ফিরব।
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাকাদামাটির হাফলাইফ - ইট পাথরের জীবন - ইমানুল হক
২০ জুলাই ২০২৪ | ২৬০ বার পঠিতবড়ো শখ করে এক দহলিজ/ কাছারি/ খানকা/ বৈঠকখানা বানিয়েছিলেন হেকিম সাহেব। সেটা আমিও দেখতে পেয়েছি। খড়ের বদল পাট দিয়ে পাঠ। দেওয়াল শোনা কথা, ডিমের লালা দিয়ে পালিশ করা। বেতের চাল। তারপরে খড়। আর দামি কাঠের হরেক কাছ। প্রতিটা খুঁটি বরগায় কাজ। লোকে দেখতো আসতো, এই শখের কাজ। দরজাও সেকালের মতো কারুকার্যময়। ঝাড়বাতি ঝুলতো। পাঙ্খাটানার ব্যবস্থাও ছিল। দহলিজের দখিন দিকে নিমগাছ। নিমের হাওয়া খাবেন, তাই।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালকিষেণজি মৃত্যু রহস্য - পর্ব ১৮ - বিতনু চট্টোপাধ্যায়
১৯ জুলাই ২০২৪ | ১৩৮ বার পঠিত'দেখুন আমাদের সমালোচনা ছিল মূলত দু'তিনটে জায়গায়। কোটেশ্বরের সাংগঠনিক ক্ষমতা, পার্টির প্রতি দায়বদ্ধতা নিয়ে কোনও কথা নেই। ওর মতো সাহসী সংগঠক পাওয়া মুশকিল। কিন্তু লালগড় আন্দোলনে ও সংযম রাখতে পারল না, তাই পার্টির মূল কাজ থেকে অনেকটা সরে গেল। ওকে আমরা বলেছিলাম, ভুল করছ। এভাবে মানুষ খুন করা ঠিক হচ্ছে না। যথেচ্ছভাবে মানুষ খুন করে দলের সংগঠনে বৃদ্ধি হবে না। বরং আমাদের সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ধারণা খারাপ হয়ে যাবে। তাছাড়া সংগঠনের বিস্তার করতে হবে গোপনে। গোপন পার্টিকে টেলিভিশন চ্যানেলে ইন্টারভিউ দিয়ে, ফোনে ইন্টারভিউ দিয়ে প্রকাশ্যে এনে দিয়েছিল কোটেশ্বর। যা আমাদের পার্টির অনেক ক্ষতি করেছে।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালতোমার বাস কোথা যে...- ১১ - Nirmalya Nag
১৮ জুলাই ২০২৪ | ৩২৮ বার পঠিত“সত্যিই তো… টেগোর কেন?” বলল বিনীতা। “ইয়েস। এই একটা প্রশ্ন লোককে হন্ট করবে। একজন জিজ্ঞেস করবে আর একজনকে - হোয়াই টেগোর? সে আবার জিজ্ঞেস করবে তিন নম্বর লোককে - হোয়াই টেগোর? এই চেন চলতে থাকবে আর দোকানের নাম ছড়িয়ে পড়বে ইন ওয়ার্ড অফ মাউথ। নতুন দোকান, তাও সেক্টর ফোরে। পাবলিসিটি তো লাগবেই,” ছদ্ম গাম্ভীর্যের সাথে বলল রঞ্জিত। “আইডিয়া আচ্ছা হ্যায়,” মাথা ঝাঁকিয়ে বলল অরুণাভ। “ওই নামের জন্যই লোকে দোকানে আসবে। আর বৃষ্টি যদি হয় তবে ছাট আসবেই,” বলল রঞ্জিত। “মানে দোকানে লোকজন এলে বিক্রিও হবে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আর ফ্যাশন…?” পুরোন কথায় ফিরে এল দাস সাহেব।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালবাংলাদেশ, বাংলাদেশ - সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায়
১৮ জুলাই ২০২৪ | ১১২১ বার পঠিতবাংলাদেশের অবস্থা যে ভয়াবহ, সে আর নতুন করে বলার কিছু নেই। ছাত্ররা গুলি খাচ্ছেন। ট্যাঙ্কও নামছে শুনলাম। আমার তালিকায় থাকা ছেলেমেয়েরা দেখছি "আন্দোলনে যাচ্ছি" লিখে রাস্তায় নেমে পড়ছেন। ইন্টারনেট নাকি জায়গায় জায়গায় বন্ধ। মেদিনিপুরের ভারত-ছাড়ো আন্দোলনের ইতিহাস মাথায় আসছে। যুবকরা পকেটে নাম-ঠিকানা লেখা কাগজ নিয়ে মিছিলে নামতেন সেই সময়। কেউ ফিরতেন, কেউ ফিরতেননা। আবু সাইদ ফেরেননি। ঢাকা তিয়েন-আন-মেন-স্কোয়ার হবে কিনা জানিনা, তবে আবুর ছবি তিয়েন-আন-মেন-স্কোয়ারের সেই যুবকের মতোই আইকনিক হয়ে গেছে। কোনো সন্দেহ নেই, হাসিনা সরকার বৈধতা হারিয়েছে। ভোটের ফলাফল যাই হোক, বিদায়ঘন্টা বাজছে। এইসব কান্ড ঘটানোর পর কোনো সরকার দীর্ঘদিন টিকে থাকতে পারেনা। এরশাদ পারেননি। সাম্প্রতিক কালে এর চেয়ে ঢের কম জনজাগরণে পশ্চিমবঙ্গেও উল্টে গিয়েছিল রাজ্যপাট। হাসিনার যাওয়াও সময়ের অপেক্ষা।
.jpg) বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাএক পা আগে, তিন পা পিছে - নরেশ জানা
১৮ জুলাই ২০২৪ | ৩৭৮ বার পঠিত২০২৪ লোকসভায় নরেন্দ্র মোদীর চারশো পারের খোয়াব যদি সত্যি সত্যি বাস্তবায়িত হত তাহলে ২০২৫ সালে আরএসএসের শতবর্ষে সংঘকে হিন্দু রাষ্ট্র উপহার দেওয়া কিংবা আইন হিসেবে মনু সংহিতাকে প্রতিষ্ঠিত করা অসম্ভব ছিল না খুব। কারণ নিজের তৃতীয় দফার সরকারে তিনি যে সংবিধান বদলাবেন এমন আভাস নরেন্দ্র মোদী নিজে এবং অমিত শাহ দিয়ে রেখেছিলেন।
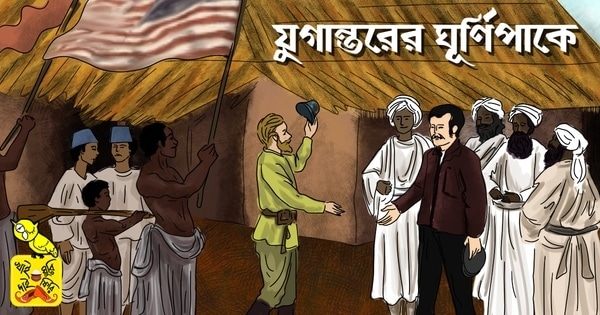 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাডেভিড লিভিংস্টোনের খোঁজে-১৪৬ - হেনরি মর্টন স্ট্যানলে
১৮ জুলাই ২০২৪ | ৪৪ বার পঠিতকিরাঙ্গোজি তার শিঙা বাজাতে থাকল, আস্টলফো১-এর জাদু-শিঙ্গার মতন প্রায় বিস্ফোরণের সম্ভাবনা দেয় আর কি! স্থানীয়রা ও আরবরা আমাদের চারপাশে ভিড় করে এলো। আর সেই উজ্জ্বল পতাকা, যার নক্ষত্রগুলি মধ্য আফ্রিকার বিশাল হ্রদের জলের উপর দুলেছিল, যেটি উজিজিতে দুর্দশাগ্রস্ত, নির্যাতিত লিভিংস্টোনের কাছে ত্রাণের প্রতিশ্রুতি হিসেবে প্রতিভাত হয়েছিল, সে আবার সমুদ্রে ফিরে এলো - ছেঁড়া অবস্থায় তা সত্য, তবে কোন ভাবেই অসম্মানিত নয়- ছিন্ন-ভিন্ন, কিন্তু পূর্ণ-সম্মানে।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালভূতডাঙার গল্প - Kishore Ghosal
১৮ জুলাই ২০২৪ | ২১৩ বার পঠিতঅশরীরীরা যখন বন্ধু হয়ে ওঠে - তারা অনেক মুশকিলই আসান করে দেয় - তেমন বন্ধু মানুষদের মধ্যে কোথায়?
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালদিলদার নগর ৭ - Aditi Dasgupta
১৭ জুলাই ২০২৪ | ৩৫০ বার পঠিতদিলদারে স্বপ্নগুলি যায়নাতো ফাঁকি। ঘটে যাওয়া সত্যিগুলি ফিরে ফিরে বলে যায় --- জীবনের আছে আরো বাকি !
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালকোটা আন্দোলন নিয়ে ৫ নোক্তা - বিপ্লব রহমান
১৭ জুলাই ২০২৪ | ৪৬৩ বার পঠিতসরকারের এ আক্রমণাত্মক আচরণে এটি স্পষ্ট যে, কোটা সংস্কার আন্দোলন ধীরে ধীরে শিক্ষার আন্দোলন থেকে সরকার বিরোধী আন্দোলনে পরিনত হওয়ায় শাসকগোষ্ঠী ভীত-সন্ত্রস্ত্র হয়ে পড়েছে। নানা রকম হামলা-মামলার মধ্যেই বছর দুয়েক ধরে চলমান কোটা আন্দোলনে এই প্রথম "স্বৈরাচার!" "স্বৈরাচার!" শ্লোগান উঠেছে।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালকোটা বিরোধী আন্দোলন (দ্বিতীয় পত্র!) - sadequzzaman sharif
১৬ জুলাই ২০২৪ | ৯৮৬ বার পঠিতধরুন শাহবাগ আন্দোলন হয়নি, গণজাগরণ মঞ্চ বলে কিছু এই দেশে হয়নি। সাকা, মুজাহিদ, নিজামি, কামরুজ্জামান সবাই এখনও এই ভূখণ্ডেই বাস করছে। জামাত আগের মতোই একটা ধরার মতো শক্তি। এমন একটা পরিস্থিতিতে কালকের ঘটনা ঘটল! অট্টহাসি চিনেন? আহ্লাদে আটখানা কাকে বলে জানেন? সব দেখতে পারতেন! পাকিস্তানের আগেরদিন নাই, থাকলে গতকাল যা হয়েছে পাকিস্তানের রাস্তায় মিষ্টি বিলানো হত। প্রকাশ্যে বিবৃতি দিত যে আমাদের কোন ভাইকে যেন অন্যায় ভাবে অত্যাচার করা না হয়! তারা আমাদের ভাই, তারা আমাদের বোন! এগুলা এক সময় নিয়ম করে দেখছি আমরা। খান...র পুলায় নায়েবে আমির মনের ভিতরের সুখানুভূতি চাপা দিয়ে গম্ভীর স্বরে টিভি ক্যামেরার সামনে বলত, খুব অন্যায় হচ্ছে! বৈষম্য দূর করে সঠিক ইশতেহার দেওয়া হোক! আমাদের কপাল ভালো যে সেই দিন দেখতে হচ্ছে না। এখন একবার চিন্তা করেন যারা রাজাকারদের ফাঁসির দাবীতে আন্দোলন করল, এই দেশে রাজাকারদের শাস্তি নিশ্চিত করল তাদের কাছেই এই স্লোগান বুলেটের মতো বিঁধছে। আর যারা সংগ্রাম করছে, যারা রাজাকাদের অত্যাচারে স্বজন হারিয়েছে, সরাসরি অত্যাচারের শিকার হয়েছে, তাদের কাছে কেমন লাগতে পারে এই স্লোগান?
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালফাস্ট বোলার “ডেমন মীনা” : ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটের বিস্মৃত এক পথিকৃৎ .... - সুচেতনা
১৫ জুলাই ২০২৪ | ২৫৯ বার পঠিত“ ওঃ নো! ডেমন মীনা আগেইন! ও যাতে এই ম্যাচে অন্তত খেলতে না পারে সে ব্যবস্থা আমাদের করতেই হবে…” ১৯৫৪ সালের টেরেন্স শোন ট্রফির দ্বিতীয় ম্যাচ খেলার আগে বিপক্ষের রোশনারা ক্লাবের মহিলা টিমের ক্রিকেটারদের তালিকায় থাকা ফাস্ট বোলারটির নাম দেখে মাথায় হাত দিয়ে বসলেন ব্রিটিশ হাই কমিশন ওমেন্স ক্রিকেট টিমের মেমসাহেব খেলোয়াড়রা! দ্রুত শুরু হল সেই পঞ্চদশী কিশোরীকে বাদ দেওয়ার জন্য নানা চেষ্টা-অপচেষ্টা!
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালদিগ্বিজয় - Tanima Hazra
১৫ জুলাই ২০২৪ | ৮৪ বার পঠিতচারপাশের দুনিয়া
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাপ্রকৃতির রুদ্রমূর্তির কাছে সুন্দরবনের আত্মসমর্পণ বিনা আর কি কোন পথ নেই! - ডঃ দেবর্ষি ভট্টাচার্য
১৫ জুলাই ২০২৪ | ৩৬১ বার পঠিতকালের নিয়মে, হিংস্র মৃত্যুদানবের উন্মত্ত নেশাতে এক সময় অবসাদ এসে জমাট বাঁধে। অহর্নিশি তোলপাড়ের ক্লান্তিতে খরস্রোতা নদীর চোখ ক্ষণিকের তরে বুজে আসে। বিধ্বস্ত চরাচরে ঝুপ করে নেমে আসে শ্মশানের স্তব্ধতা। গোবর নিকানো আদুরী উঠোনময় শুধু চরে বেড়ায় স্মৃতির বিধ্বংসী খণ্ডচিত্র। সুন্দরবনের মানুষদের আছেটাই বা কি, যে হারাবে! কিঞ্চিত জমি-জিরেত, খান কয়েক গবাদি পশু, স্বপ্ন বোঝাই ডিঙি নৌকো, আর নদীর ওপারের ভয়াল বাদাবন।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালপাহাড়ের খাঁজ - upal mukhopadhyay
১৪ জুলাই ২০২৪ | ৯১ বার পঠিত হরিদাস পাল
হরিদাস পালরুবাইয়াত ও কয়েকটি রাত - swagatam sen
১৪ জুলাই ২০২৪ | ২৮২ বার পঠিতশিক্ষকপ্রতিম লেখক কুণাল বসুর পরামর্শে আমিন মালুফের লেখা পড়তে শুরু করেছি। আমি অশিক্ষিত পাঠক। কেউ যেন আবার "এদ্দিনে পড়লেন" ভেবে মনে মনে উপহাস শানাবেন না দয়া করে। গরীবের ঘোড়ারোগের মত অশিক্ষিত পাঠক উচ্চাঙ্গের লেখা পড়ে ফেলে ভারী অস্বস্তি বোধ করে। অনুভূতি বোঝানোর ভাষা নেই। মতামত দেবার যোগ্যতা নেই। সব চলে গেলে পড়ে থাকে কিছু রাবিশ লেখার ইচ্ছা। যেমন তেমন নয়। অনুপ্রাণিত রাবিশ।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালতাঁর সিলেট ভ্রমণ! - sadequzzaman sharif
১৪ জুলাই ২০২৪ | ২২৮ বার পঠিতএদিকে এক ইংরেজ সাহেব আসছেন, তিনিও পরেরদিন এই ট্রেনে সিলেট যাবেন। কিন্তু প্রথমশ্রেণীতে উঠতে গিয়ে শুনলেন এখানে তিনি আছেন, অন্য কামরাগুলোতেও তাঁরই লোকজন, তখন সাহেব তাঁদের ঘুমের ব্যাঘাত করা ঠিক হবে না ভেবে স্টেশনের বিশ্রামাগারে বসেই রাত কাটিয়ে দেন। তিনি কোন সময় কুলাউড়ায় এসে পৌঁছবেন এইটা হিসাব করে সিলেট থেকে অগ্রগামী এক দল রাতেই এসে হাজির হয়েছিলেন কুলাউড়ায়, সিলেটের স্বনামধন্য সব ব্যক্তিবর্গ। সবাই রাত কাটালেন স্টেশনে। কুলাউড়ায় পরেরদিন লোকে লোকারণ্য! সবাই ফুল মালা নিয়ে হাজির। একনজর দেখতে চায় সবাই। এর মধ্যে সিলেট থেকে আগত ওয়েলস প্রেসবিটেরিয়ান চার্চের মিসেস ইথেল রবার্টস রেলের কামরায় এসে কথা বলে গেলেন। সিলেটে তাঁদের বাড়িতেই উনার থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। তাঁরা বাড়ি ঘর ছেড়েই ক্ষান্ত হন নাই, কুলাউড়ায় এসে দেখাও করে গেলেন! কুলাউড়ায় দেওয়া হল আরেক সংবর্ধনা। উপচে পড়া ভিড়ের মাঝে ট্রেন চলল সিলেট মুখি।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালপাঙ্খাবাড়ি রোড - upal mukhopadhyay
১৩ জুলাই ২০২৪ | ১৩৯ বার পঠিত বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজামহারাজ ছনেন্দ্রনাথ, খেলনাবাড়ি আর পক্ষীরাজ ঘোড়ার গল্প - রমিত চট্টোপাধ্যায়
১৩ জুলাই ২০২৪ | ৫২৭ বার পঠিতছেনু দেখল, সত্যিই তো, পকাইকে তো এবার চড়তে দিতেই হয়, বেচারি এতক্ষণ ধরে অপেক্ষায় রয়েছে। তার ওপর ওরই ঘোড়া যখন। আজ সকালে পকাইদের বাড়ি এই ঘোড়াখানা আসতেই পকাই তাড়াতাড়ি ছেনুকে ডেকে এনেছে। সেই ঘোড়াখানা দেখেই তো ছেনু আনন্দে আত্মহারা। উফ্, ঘোড়া বটে একখানা। কি সুন্দর লালের ওপর সাদা,কালো, হলুদ দিয়ে রং করা, পিঠের উপর চওড়া করে বসার আসন পাতা, ঘাড়ের কাছে কেশরের পাশ দিয়ে আবার ধরার জন্য দুটো হাতল রয়েছে, খাড়া খাড়া কান, সাথে তেমনি টানা টানা চোখ - দেখেই চোখ জুড়িয়ে চায়। এ যা ঘোড়া, পক্ষীরাজ না হয়ে যায় না! সত্যিই, মহারাজ যেন এমন একটা ঘোড়ারই সন্ধানে ছিলেন এতদিন ধরে। তাই সে ঘোড়া দেখে আর লোভ সামলাতে পারেননি, পকাইয়ের জন্য আনা ঘোড়ায় নিজেই টপ করে বসে পড়েছেন। আর ঘোড়ায় চেপে টগবগ টগবগ করে সেই যে ছুটিয়েছেন, ডানা মেলে এদিক ওদিক ঘোরার মধ্যে আর সময়ের হুঁশ ছিল না। পকাই ধৈর্য হারিয়ে আবার ঘরে চলে গিয়েছিল, ফিরে এসেও যখন দেখল মহারাজের ঘোড়ায় চড়া শেষ হয়নি, তখন চিৎকার জুড়তেই ছেনুর টনক নড়ল।
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাবিপ্লবের আগুন - পর্ব তেরো - কিশোর ঘোষাল
১৩ জুলাই ২০২৪ | ২৩৫ বার পঠিতজনা খুব দৃঢ় স্বরে বললে, “বিপদকে আমরা ভয় পাই না”। ভল্লা তাচ্ছিল্যের হাসি মুখে নিয়ে বলল, “খুব আনন্দ পেলাম শুনে। আসন্ন বিপদকে যদি কেউ বুঝতেই না পারে, সে বিপদকে ভয় পাবে কেন? একটি শিশু যখন জ্বলন্ত প্রদীপের শিখা ধরতে যায়, তাকে সাহসী বলব, না বীর বলব, আমি আবার ঠিক বুঝে উঠতে পারি না”।
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাঅন্য এক আগুনের গল্প - ঝানকু সেনগুপ্ত
১৩ জুলাই ২০২৪ | ২৪৩ বার পঠিত বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাপাঁচটি কবিতা - শিশির আজম
১৩ জুলাই ২০২৪ | ১২৫ বার পঠিততারুন্য পেরিয়ে এসে এখন আমি জানতে চাই কাকে বলে স্তন, / আর স্তনমন্ডল? / আমার কুকুরগুলো তোমার স্তনের দিকে তাকিয়ে থাকে / তাকিয়ে থাকে / বরফের ছাদের নিচে; মাকড়শা জাল বিছিয়েছে তোমার স্তনের ত্বকে।/ / আকর্ষণীয় না হোক, তবু আমার শরীর আছে । আমার শরীর থেকে/ তোমার শরীরে পৌছতে/ যে সেতু দরকার তা নির্মাণ করতে আমি মিন্ত্রী পাবো কোথায় ? / / টাকাপয়সা আর সামাজিক সম্পর্কের দাম আছে। কিন্তু আরও সময় নিতে/ আমি রাজি, / লিওনার্দোর মোনালিসা আর বতেরোর মোনালিসা যে আলাদা দুজন/ আলাদা সন্দেহজড়িত মেঘ আর উইনিং কন্ট্রাসেপশান, / এটা স্বীকার করে জানতে চাই/
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাকাদামাটির হাফলাইফ - ইট পাথরের জীবন - ইমানুল হক
১৩ জুলাই ২০২৪ | ৩৫৩ বার পঠিতএকটা কথা আছে, শিশুরা ফুলের মতো সুন্দর। অবশ্যই। মিষ্টি হাসি, আধো আধো কথা। প্রিয়জনকে দেখলেই ছুটে আসা। কিন্তু ছোটদের মধ্যে নিষ্ঠুরতাও থাকে। সময় ও সমাজের প্রভাবে মানবিক হয়ে ওঠে। মানবিক নয়, বলা উচিত প্রাণবিক। পৃথিবীর সকল প্রাণীর মধ্যে নিষ্ঠুরতা কাদের মধ্যে বেশি?
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালদমন - পাপাঙ্গুল
১৩ জুলাই ২০২৪ | ১৯৮ বার পঠিতএই কেল্লার ভেতর একখানা নতুন গির্জা , স্কুল , খেলার মাঠ এইসব আছে। শনিবার বলে সবই বন্ধ। সেখান থেকে আবার দেবকা সৈকতে এসে টানা পাঁচিলের ওপর বসে আরব সাগরের হাওয়া খাওয়া গেল। সাবুর পাঁপড় , ঝালমুড়ি , টকঝাল চানাচুর এইসব ফেরিওয়ালারা ঘোরাঘুরি করছে। এই সৈকত রোজ পরিষ্কার করা হয় বলে মনে হল , প্লাস্টিক বা অন্যন্য নোংরা নেই। একজায়গায় ধাপ ধাপ করা আছে সৈকতে নামার জন্য। সেখানে দুখানা চৌকো বারান্দাওলা ঘরের মধ্যে কিছু জলখাবারের কাউন্টার, এছাড়া কোনো স্থায়ী খাবারের দোকান নেই। একটু আগে যে নির্মীয়মাণ রাস্তা দিয়ে দেবকা সৈকতে এসেছি, সেখানেই ফেরত যেতে হল তন্দুরি পমফ্রেট ইত্যাদি খাবার জন্য। এই রাস্তার দুধারে যাবতীয় হোটেল , খাবার জায়গা , ট্যাটু পার্লার ইত্যাদি। রাস্তাতেও ট্যাটু করানোর জন্য কেউ কেউ বাক্স নিয়ে বসে আছে।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালবৈঠকি আড্ডায় ২০ - হীরেন সিংহরায়
১৩ জুলাই ২০২৪ | ৬০৪ বার পঠিতজীবনের হাল না ভেঙ্গে যে নাবিক সঠিক দিশায় উপনীত হয়ে নৌকো বা জাহাজ থেকে নেমে কোন বন্দর অতিক্রম করেন, সেই অভিযানকে ইতালিয়ানে বলা হয়েছিল – পেরিয়ে বন্দর বা ‘ পাসে পোরত’ যা থেকে পাসপোর্ট কথাটা এসেছে। ফরাসিরাও অবশ্য এ শব্দের পিতৃত্ব দাবি করে থাকেন বলে শোনা যায় । জার্মান সহ বহু ইউরোপীয় ভাষায় তার নাম শুধু ‘পাস’- অতিক্রম ।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালটাকা পয়সা যত নষ্টের মূল - দ
১২ জুলাই ২০২৪ | ২৮৬ বার পঠিত হরিদাস পাল
হরিদাস পালইসলামের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ১ - Eman Bhasha
১২ জুলাই ২০২৪ | ১৭৩ বার পঠিতইসলাম প্রতিষ্ঠার ইতিহাস। লক্ষ্য, কর্মসূচি ও আজকের মৌলবাদী প্রবণতা এবং সাম্প্রদায়িকতা
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালযদিদং মোচ্ছব তব - যদুবাবু
১২ জুলাই ২০২৪ | ২১৮১ বার পঠিতআপনি ভাববেন, আমজনতার কি এইসব দেখে রাগ হয়? হিংসে হয়? ছিনিয়ে খেয়ে নিতে ইচ্ছে করে? নাঃ। হয় না। কিস্যু হয় না। যারা বলে হয় তারা আঁতেল না হয় হাপ্প্যান্ট। শুনুন, হিংসে হয় সমানে-সমানে, বা সামান্য একটু উপরের লোকের উপর, তাকে একটু টেনে নামালে তৃপ্তির ঢেঁকুর ওঠে। আম্বানি কি আদানি সেই সব সীমার বহু বহু উর্ধ্বে। এদের জন্য হিংসে তো দূরস্থান, মানুষের মনে যা থাকে তার নাম একপ্রকার ভালোবাসা-ই। অ্যাডাম স্মিথ একে বলেছিলেন, “পিকিউলিয়ার সিম্প্যাথি” – অদ্ভুত সমবেদনা। আম্বানি-আদানির উচ্চাশা ও লোভ – কী করে যেন পরিণত হয়ে যায় আবাল জনতার উচ্চাশায়। আমাদের দেশ বিশ্বের ধনীতম হওয়ার ধারেকাছেও নেই তো কি আছে, আরে বাবা ধনীতম ব্যক্তিটি তো আমার-ই দেশের। তাই আমরা গৌরবে বহুবচ্চন। আর আহা, এই এতো বড়ো বড়ো বিষ বিলিওয়নেয়ার বড়োলোক, ওরাই যদি এমন বৎসরব্যাপী মোচ্ছব না করে তো করবেটা কে? ও পাড়ার পিন্টুদা?
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালকিষেণজি মৃত্যু রহস্য - পর্ব ১৭ - বিতনু চট্টোপাধ্যায়
১২ জুলাই ২০২৪ | ৫৮৫ বার পঠিতএকদিন বিকেলে অফিসে বসে আছি। পরিচিত এক ব্যক্তি বান্দোয়ান থেকে ফোন করলেন। এলাকার পরিস্থিতি নিয়ে কথা হল। বললেন, পরীক্ষার জন্য বড়ো মিটিং বন্ধ আছে, কিন্তু পরিস্থিতি খুব খারাপ। কেন? বললেন, পুরো আতঙ্কের পরিবেশ। বিধায়কই বাড়িতে থাকতে পারছেন না, আর আমাদের কী হবে? তাঁর কথা শুনে একটু অবাক হলাম। জিজ্ঞেস করলাম, মানে? তিনি বললেন, বান্দোয়ানের এমএলএ বাড়ি থেকে লুকিয়ে রাতে একটা লাইব্রেরিতে গিয়ে থাকেন মাওবাদীদের ভয়ে।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালধ্যান কেন বিজ্ঞানের আলোচনার বিষয় হতে পারে তাই নিয়ে দু চার কথা - অরিন
১২ জুলাই ২০২৪ | ৬৮৬ বার পঠিতধ্যান কেন বিজ্ঞানের আলোচনার বিষয় ও কেন ধ্যান কি নিয়ে স্নায়ুবিজ্ঞানের আলোচনার আগে এই কথাগুলো লেখার প্রয়োজন । এটি প্রথম পর্ব বলে ধরে নেয়া যেতে পারে ।
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাগুরুতে ছবি দেওয়া যাবে কী করে? - টেকনোচণ্ডাল
১১ জুলাই ২০২৪ | ৩২৮ বার পঠিতগুরুচণ্ডা৯-তে আপনার কমেন্ট বক্সে বা লেখার পাতায়, হরিদাস পাল হোক কি খেরোর খাতা, কেমন করে ছবি জুড়বেন। একসময় এই কাজটি সরাসরি করা যেত। ভবিষ্যতেও আবার তাই করা যাবে আশা করা যায়। কিন্তু বর্তমানে আমাদের একটু ঘোরানো পথে কাজটি সারতে হচ্ছে। কেমন করে? জেনে নিন এখানে আর তারপর ঝপাঝপ ছবি আটকে দিন গুরুচণ্ডা৯-র পাতায়।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালতোমার বাস কোথা যে...- ১০ - Nirmalya Nag
১১ জুলাই ২০২৪ | ৩৪৬ বার পঠিতযথাসম্ভব শব্দ না করে ড্রেসিং টেবিলের সামনে থেকে চিরুনি তুলে নিয়ে সে গেল বারান্দার খোলা দরজার দিকে। এই বারান্দার সামনে একটা মুসান্ডা আর একটা হলুদ জবা গাছ আছে। দরজাটা বাইরের রাস্তা থেকে খুব চোখে পড়ে না। তাই এইখানে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়ায় বিনীতা, চিরুনিতে চুল উঠে এলে সেগুলো আঙুলে পাকিয়ে ঘরের কোণে রাখা ঢাকনা দেওয়া ছোট ডাস্টবিনে ফেলে দেয়। আজও তাই করতে যাচ্ছিল, এমন সময়ে বাড়ির সামনে একটা গাড়ি এসে থামল
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালএকটি বুকস্টল ও একটি শহর - Samir Ghosh
১০ জুলাই ২০২৪ | ৪৫১ বার পঠিতগর্জে উঠেছে অক্ষর শহর শ্রীরামপুর। ‘শ্রীরামপুর রেলওয়ে স্টেশন বুক স্টল' বন্ধ করা যাবে না এমন দাবি তুলে সরব হয়েছেন এ শহরের বিখ্যাত কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, মানবাধিকার কর্মীরা।
- আরও বুলবুলভাজা ... আরও হরিদাস পাল ...
-
গুরুচণ্ডা৯-র গ্রাহক হোন
কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে গুরুচণ্ডা৯-র গ্রাহক হোন। গুরুচণ্ডা৯তে প্রকাশিত লেখাগুলি পেতে চাইলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যুক্ত হোন, অথবা, আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলটির গ্রাহক হোন।
- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই
- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... PRABIRJIT SARKAR, অমিতাভ চক্রবর্ত্তী)
(লিখছেন... অমিতাভ চক্রবর্ত্তী)
(লিখছেন... কচ্ছপ, Debasis Bhattacharya, Debasis Bhattacharya)
(লিখছেন... অমিতাভ চক্রবর্ত্তী, মোহাম্মদ কাজী মামুন , Kishore Ghosal)
(লিখছেন... অভিজিৎ। , অমিতাভ চক্রবর্ত্তী, অভিজিৎ। )
- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন
(লিখছেন... )
(লিখছেন... অসিতবরণ বিশ্বাস , দ, aranya)
(লিখছেন... দ)
(লিখছেন... aranya , হীরেন সিংহরায়, পাপাঙ্গুল)
(লিখছেন... r2h, Guru)
- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... :|:, রঞ্জন , :|:)
(লিখছেন... ., Guru, Guru)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... দীপ, দীপ , ar)
(লিখছেন... কৌতূহলী, Debasis Bhattacharya, কৌতূহলী)
- কি, কেন, ইত্যাদি
- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...
- আমাদের কথা
- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...
- বুলবুলভাজা
- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...
- হরিদাস পালেরা
- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...
- টইপত্তর
- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...
- ভাটিয়া৯
- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...