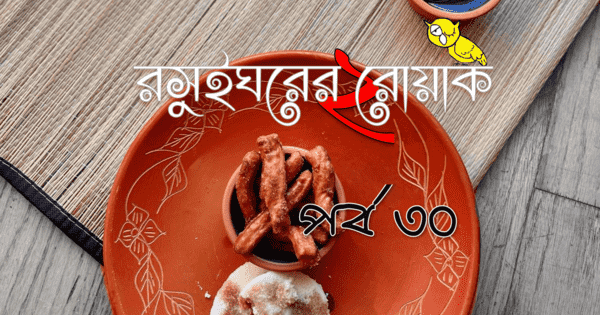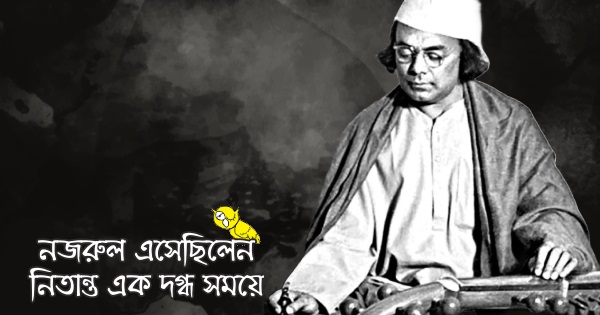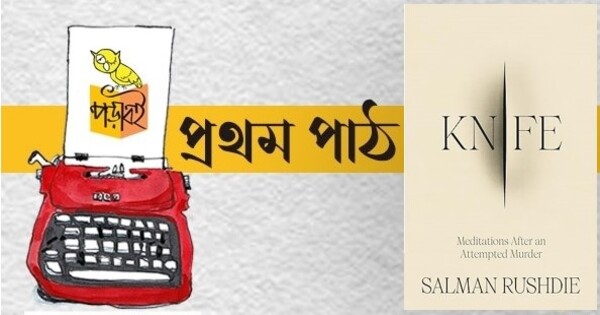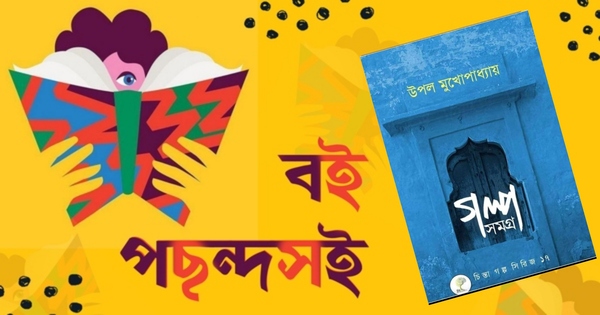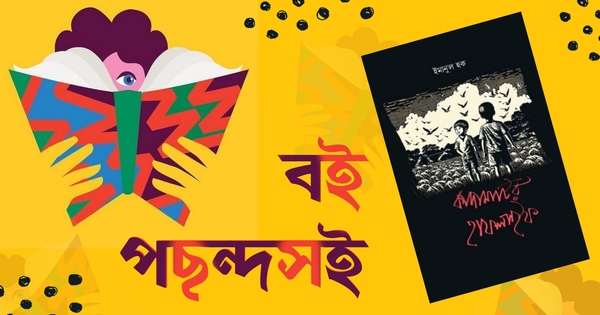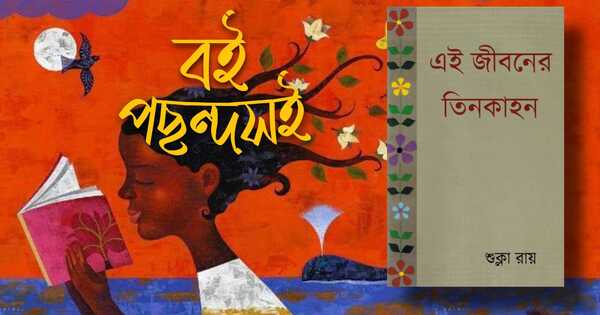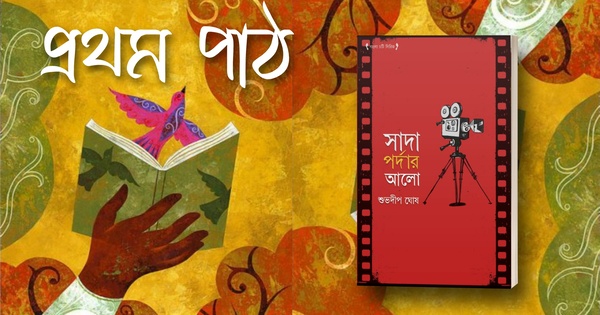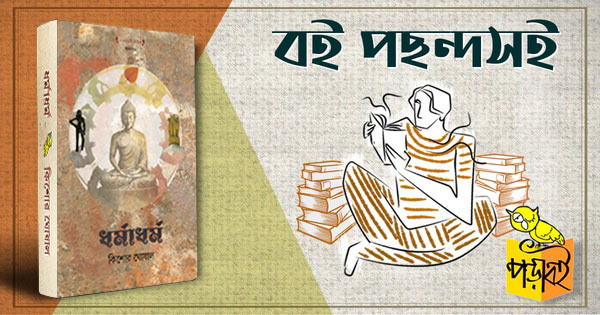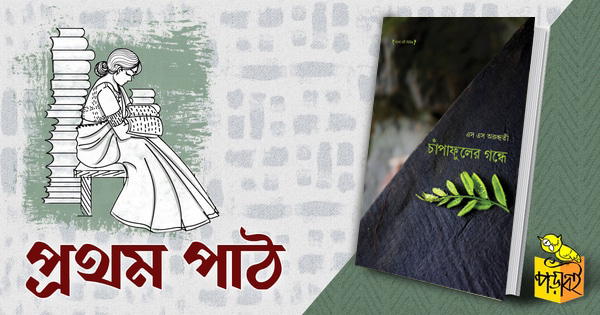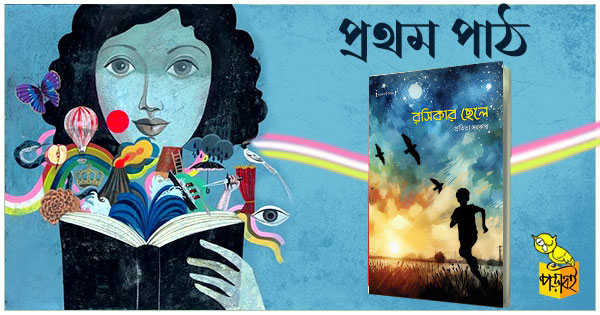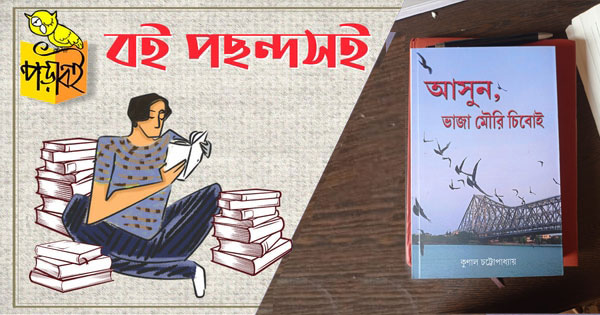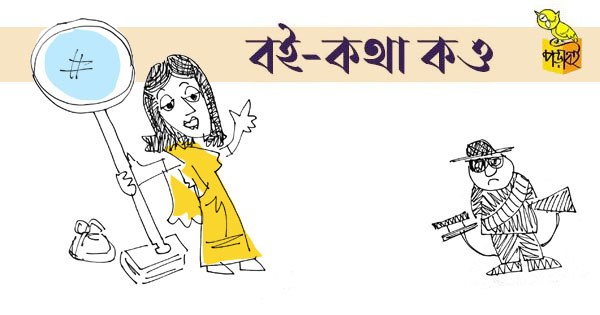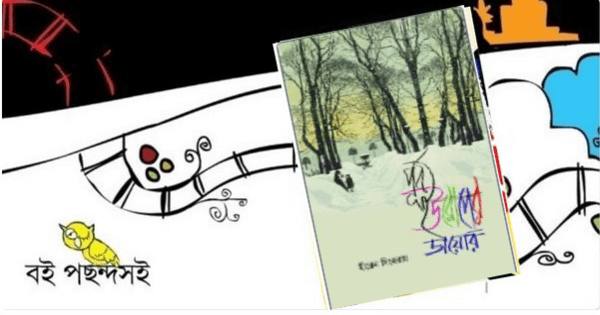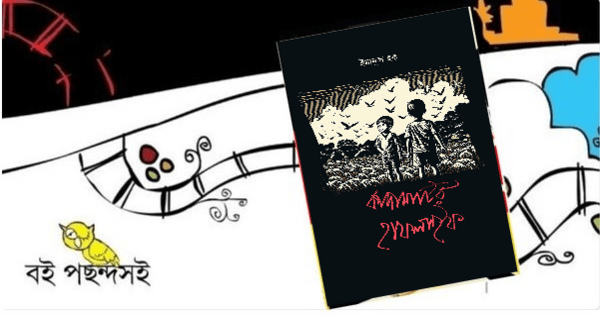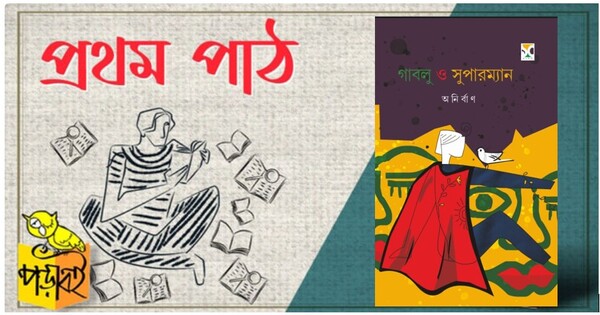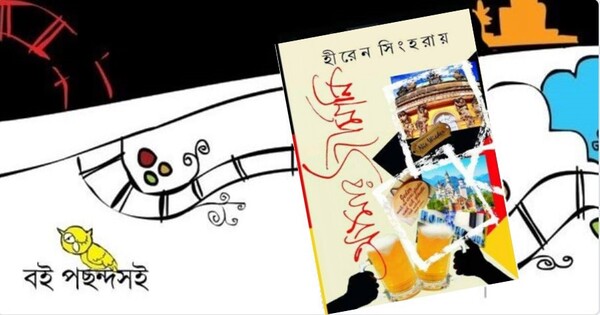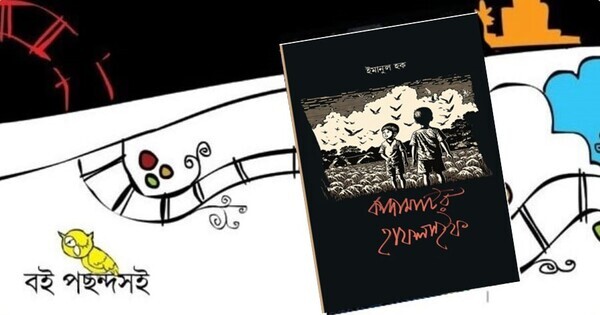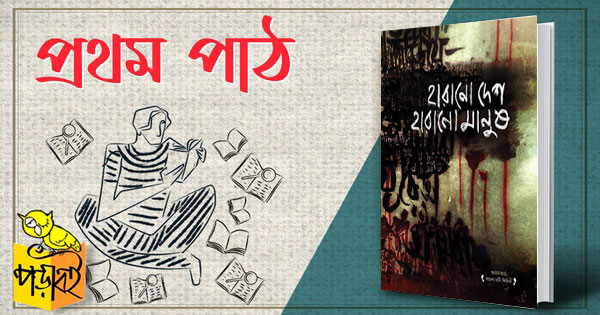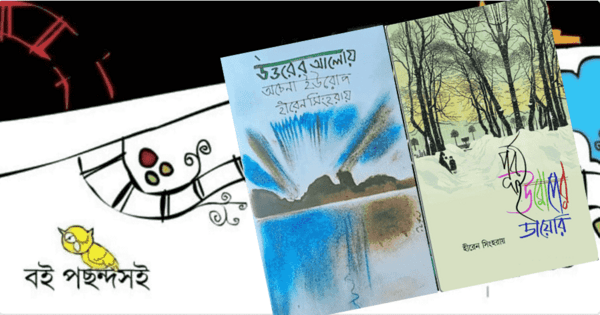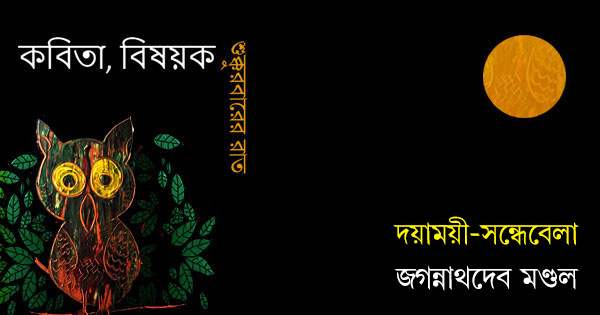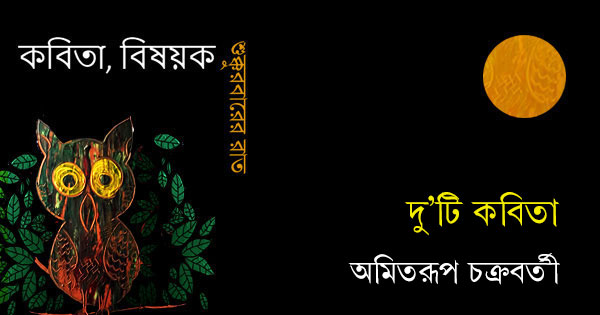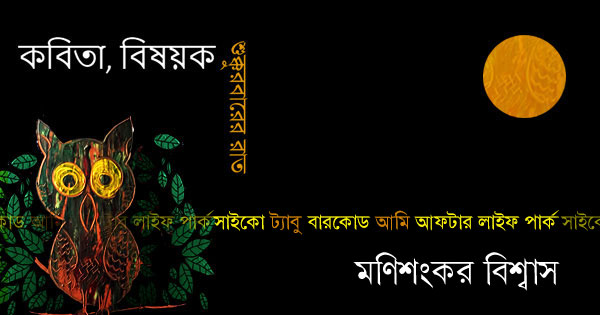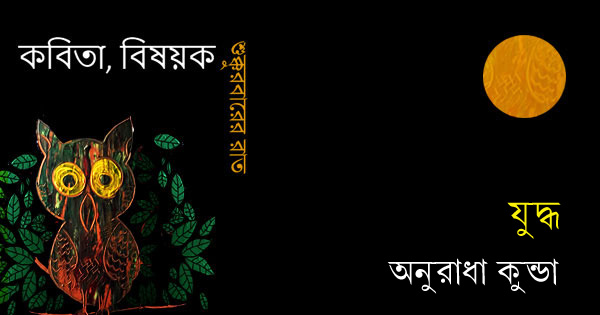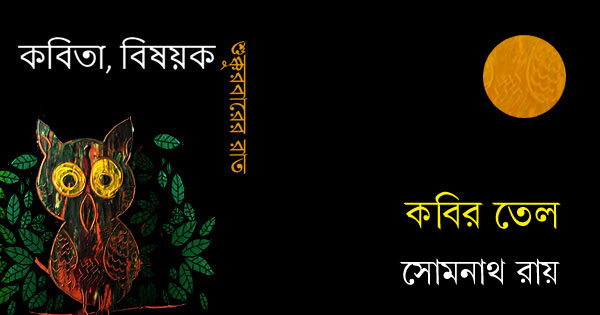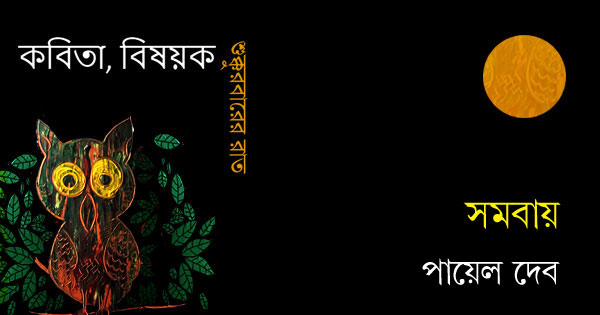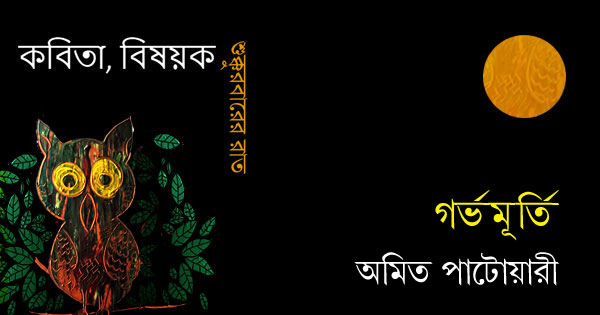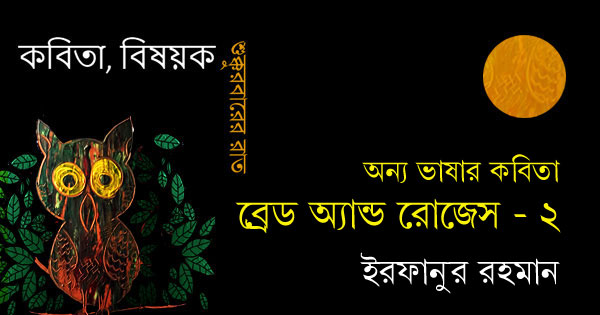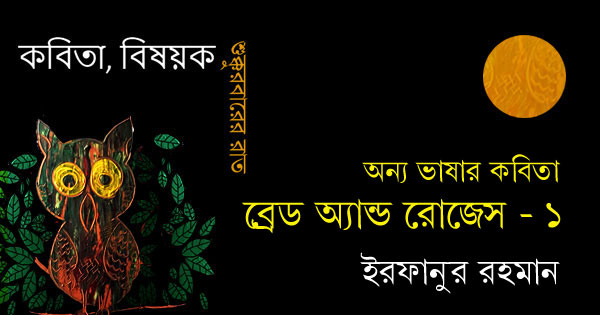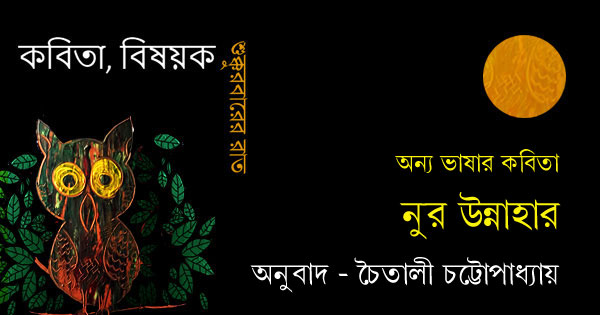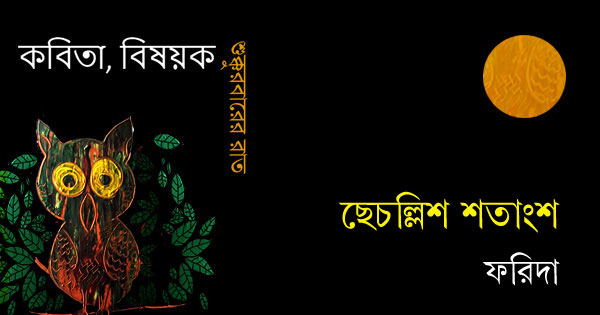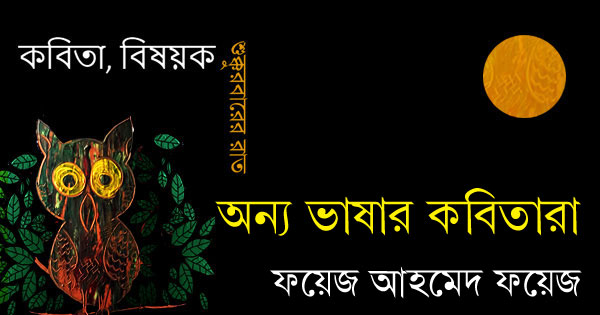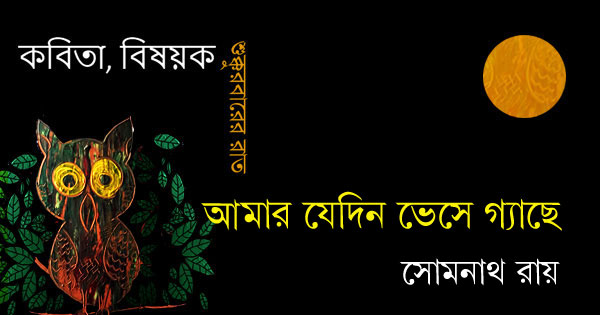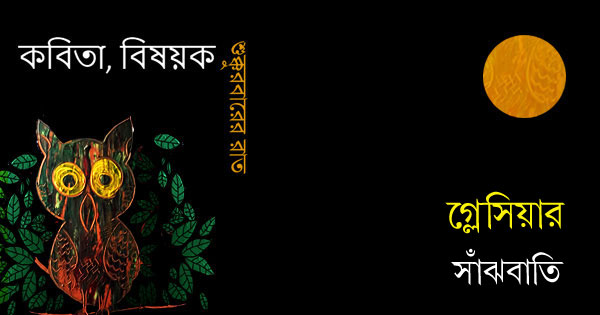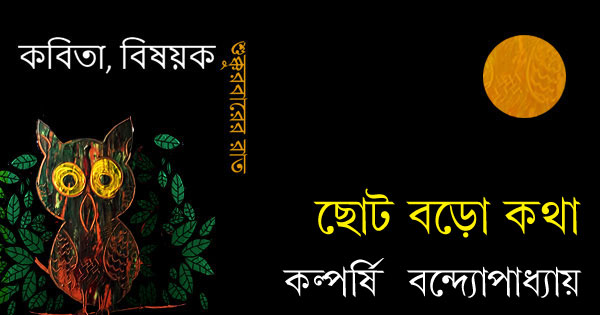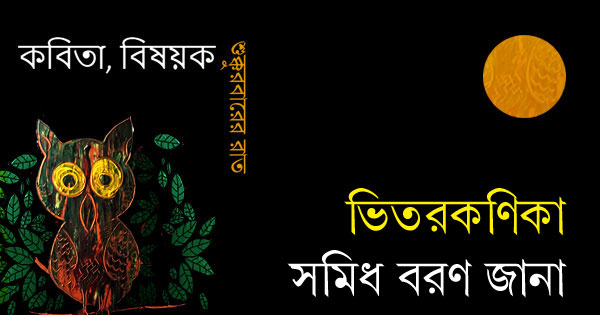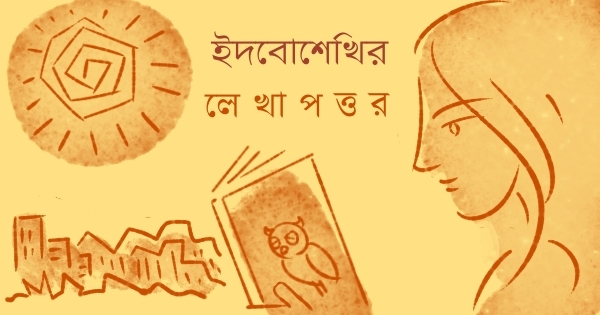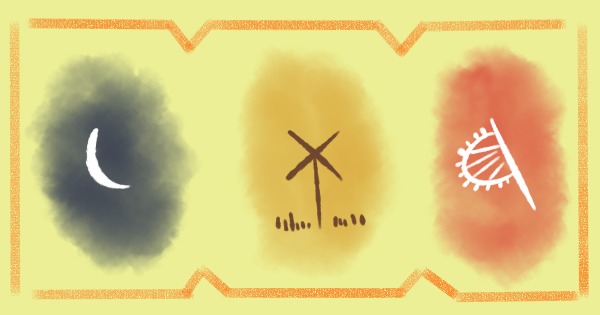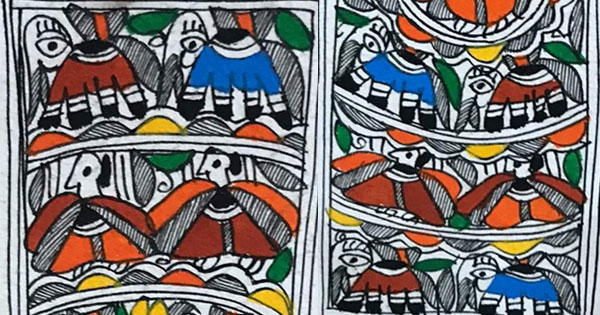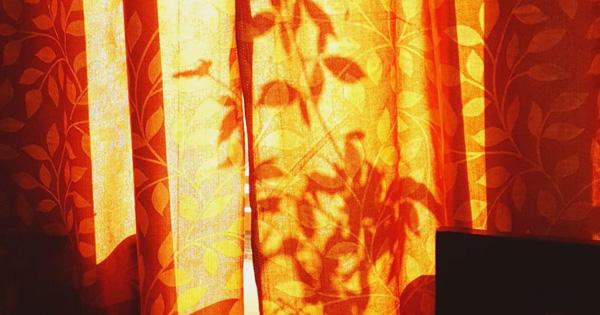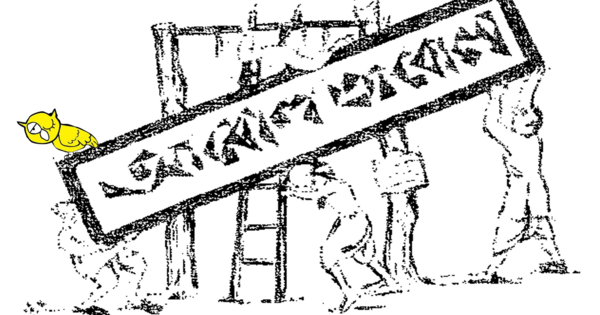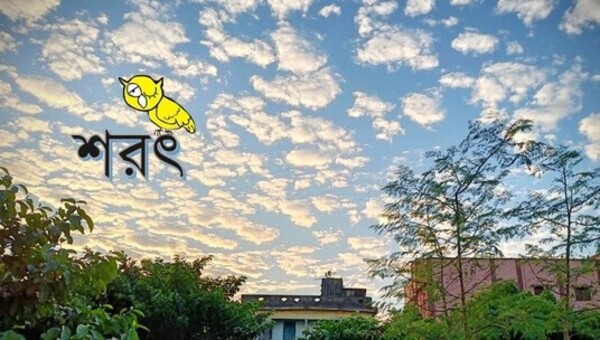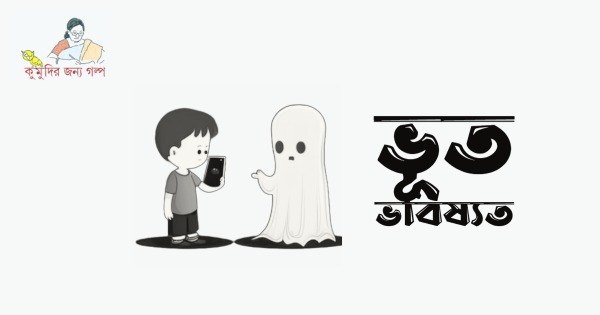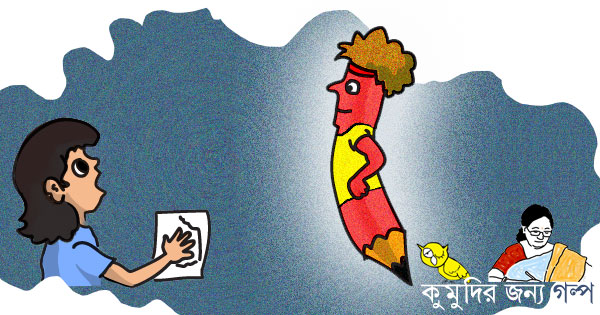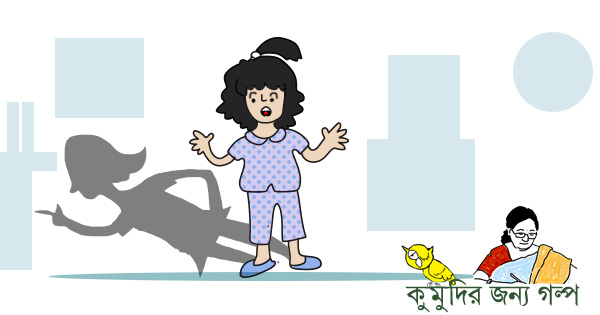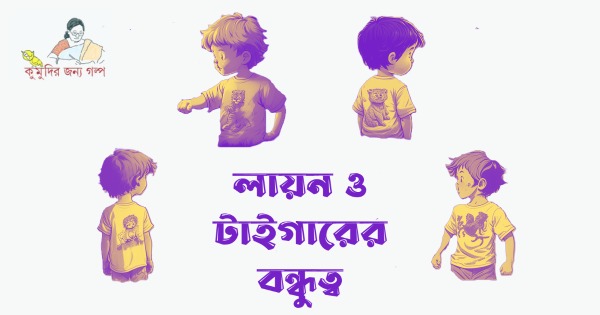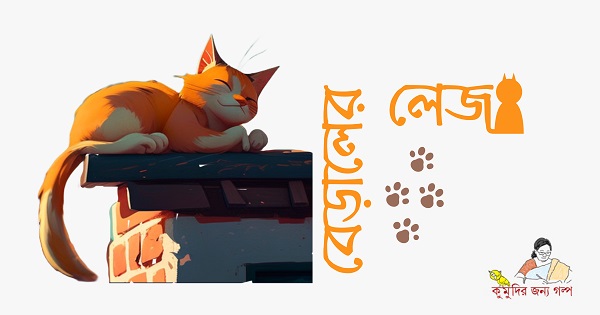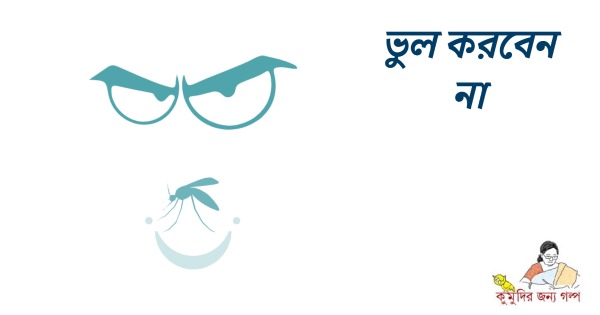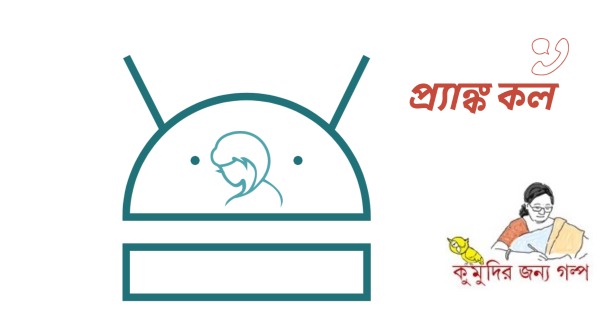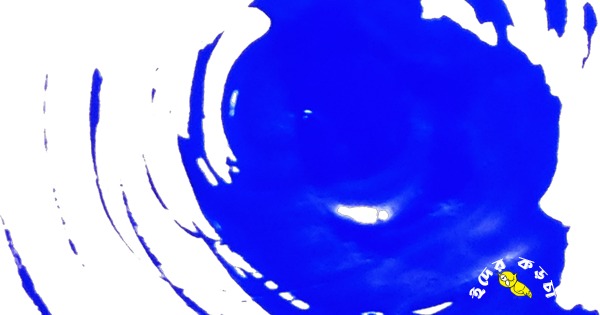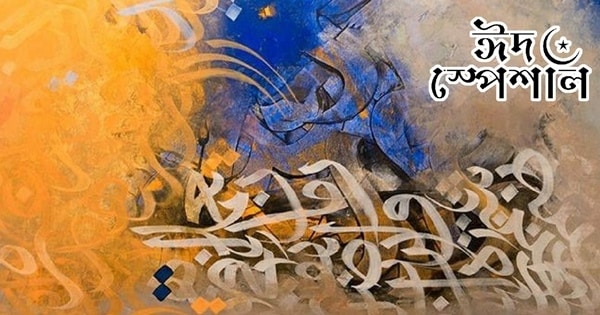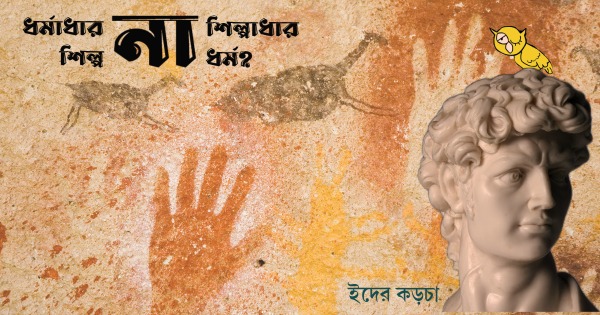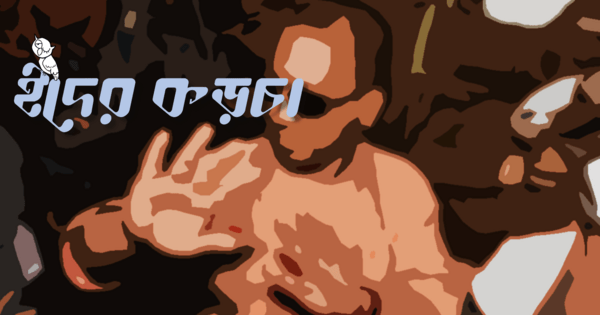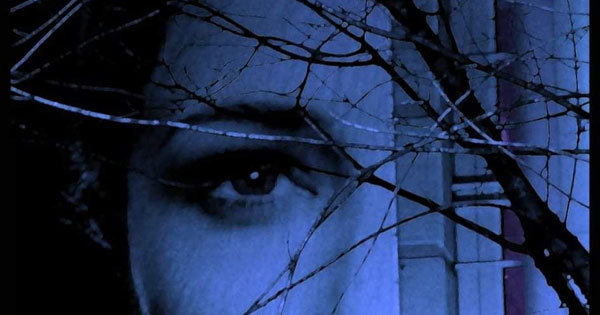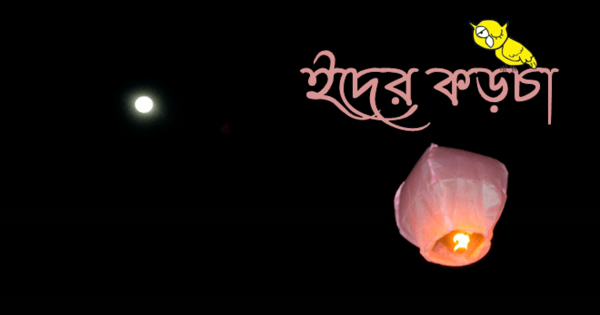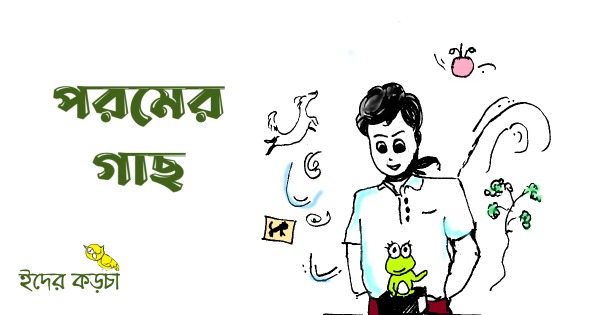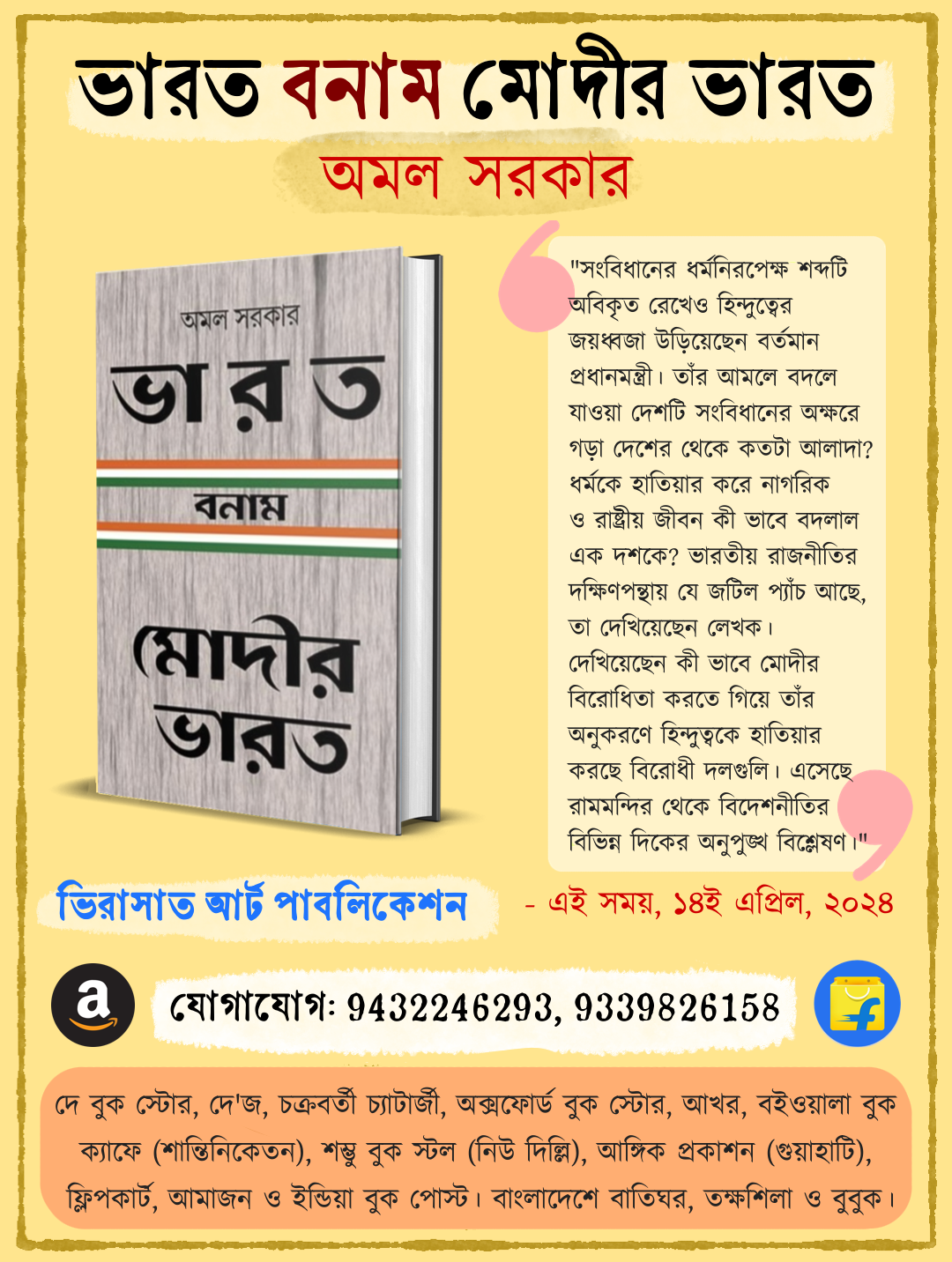তাজা বুলবুলভাজা...
অন্ধ ও বধিরের দেশে? - প্রতিভা সরকার | বাস্তব আর কল্পনা কোথায় যে হাত ধরাধরি করে চলতে শুরু করবে কেউ জানে না। আসলে তাই-ই তো স্বাভাবিক। কল্পনার পা থাকে বাস্তবের বুনিয়াদে, বাস্তব নিয়ন্ত্রিত অথবা অনিয়ন্ত্রিত হয় কল্পনার লাগামে অথবা লাগামহীনতায়। গুরুচন্ডা৯তে অমিতাভ চক্রবর্তীর খড়্গপুর আইআইটির ছাত্র ফয়জান আহমেদের মৃত্যুর ওপর সুলিখিত প্রতিবেদনটি পড়ে এইরকম মনে হল। এই নির্মম ঘটনাগুলো নিয়ে কাজ করতে গেলে মানুষকে অনেক অবিশ্বাস্য নিষ্ঠুরতা, গোপন রক্তপিপাসার মুখোমুখি হয়ে বিহবল হয়ে যেতে হয়। অবাক লাগে ভাবতে যে এই ধরনের কাজের অনেকগুলোই অবিশ্বাস্য দ্রুততায় করে ফেলে যারা, তারা সবাই কিন্তু ভাড়াটে খুনি বা সাইকোপ্যাথ নয়। তারা অনেক সময়ই মধ্যবিত্ত ঘরের দুধ ঘি খাওয়া মেধাবী ছেলে। আমাদের সন্তান। সমাজের সবচেয়ে সুবিধাভোগী অংশ। দারিদ্র নয়, সেকারণে নীতিহীনতাও নয়, নিষ্ঠুরতার জন্যই নিষ্ঠুরতা কী করে তাদের বীজমন্ত্র হয়ে ওঠে, কে জানে! কেন এত কথা? শোনা যায় ফয়জানের মৃত্যু আত্মহত্যা বলে চালিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল কর্তৃপক্ষ এবং মেডিকেল কলেজও। কিন্তু সদ্য প্রকাশিত দ্বিতীয়বারের ময়না তদন্তের রিপোর্টে পরিষ্কার বলা হয়েছে, এটি আত্মহত্যা নয়, মাথার পেছন দিকে এবং বুকে প্রচুর রক্তক্ষরণের ফলে মৃত্যু ঘটেছে আসাম থেকে আগত এই মেধাবী তরুণের। আরও জানা গেছে, তার ঘাড়ে গুলির দাগ আছে। মৃত্যু নিশ্চিত করতে প্রবল প্রহার করে তারপর গুলি করা হয়েছিল ফয়জানকে? স্মর্তব্য, এই দ্বিতীয় বারের ময়না তদন্ত হয়েছে হাইকোর্টের নির্দেশে। নাহলে সব ধামাচাপা পড়েই থাকত। গুরুচন্ডা৯ প্রকাশিত রসিকার ছেলে উপন্যাসে রোহিত ভেমুলার ছায়ায় গড়া কেন্দ্রীয় চরিত্র রোশনের পাশে আছে ফয়জান, স্বনামে নয়, তার নাম ওখানে ফয়জল। তার মৃত্যুর পর মা ছুটে এসেছেন অতদূর থেকে। তাঁর সঙ্গে কেমন ব্যবহার করেছে কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় পুলিশ, তার বর্ণনা আছে। সেই সময় প্রকাশিত বিভিন্ন কাগজের রিপোর্ট ঘেঁটে লেখা। ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে অনেকের ইন্টারভিউ নিয়ে তারপর তিলে তিলে গড়া হয়েছে এই দুর্ভাগা তরুণের চরিত্র। তাকে দাঁড় করানো হয়েছে রোহিত ভেমুলার পাশে। প্রখ্যাত সাহিত্যিক সাধন চট্টোপাধ্যায় এই ২০১৬ এবং ২০২২ কে এক সুতোয় গেঁথে ফেলাকে অন্যায়ের প্রবহমানতা দেখাবার পক্ষে খুবই কার্যকরী হয়েছে বলে ভেবেছেন। আমরা পড়ে দেখতে পারি উপন্যাসের কিছুটা অংশ, যেখানে মায়ের চোখের জল আর প্রবল আকুতি বৃথা হয়ে যাচ্ছে। এমপ্লুরা নামের রাসায়নিক দিয়ে যে নরপশুরা ফয়জানের মৃতদেহ অবিকৃত রাখবার চেষ্টা করেছিল, তাদের নির্লিপ্ততা। রসিকার ছেলে প্রকাশ করে গুরুচন্ডা৯ যে সামাজিক যুদ্ধের সূচনা করেছে, তাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে অমিতাভ চক্রবর্তীদের প্রতিবেদন। রসিকার ছেলে থেকে উদ্ধৃতি“আইআইটিতে নেমে প্রথমে ফতিমা আন্টিকে গেস্ট হাউজে তুলল রোশন। দুজনেই হতবুদ্ধি, শোকে উন্মাদ, তার মধ্যে রোশনই সম্পূর্ণ কান্ডজ্ঞান হারায়নি। কাউকে না কাউকে তো খোঁজ খবর নিতে হবে। থানায় যেতে হবে, ডিরেক্টরের সঙ্গে কথা বলতে হবে। পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট, ডেথ সার্টিফিকেট এরা আগেই অন লাইন পাঠিয়ে দিয়েছে। রোশন না ভেবে পারে না যে ফিজুর শরীর এখন মাটির নীচে মাটি হয়ে যাচ্ছে। তাদের গ্রামে নতুন কবর হলে সবসময় তা বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়। পেছনে ফেলে যাওয়া মানুষের স্নেহ আর যত্নের মতো মৃতকে আগলে রাখে ঐ বেড়া। স্বজনরা এসে বেড়ার এপাশে দাঁড়িয়ে বা বসে কান্নাকাটি করে, কখনও মৃতের সঙ্গে কথা বলে নিজের মনে। তারপর কালের নিয়মে শোক প্রশমিত হয়, বেড়া জীর্ণ হয়ে মাটিতে মিশে যায়। তবু যেন কিছু থেকে যায়! বড় কোমলতা আর ভালবাসা মাখা এই বিদায় জানানোর পদ্ধতি! কিন্তু বিদেশে বিভুঁইয়ে কোথায় যে ফিজুকে এরা কবর দিয়েছে, কোন কবরিস্তানে, তা পর্যন্ত এখনও দেখা হয়নি তাদের। ছবিতে তো সব বোঝা যায় না।যে ছেলে আগের সন্ধেয় কথা বলেছে রোশনের সঙ্গে, পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট অনুযায়ী হিসেব কষে দেখা গেল, পরের পনের/ষোল ঘন্টার মধ্যে তার মৃত্যু হয়েছে। মাত্র পনের/ষোল ঘন্টা ! একটা গোটা দিনও তো নয়!রাতে ছ’ সাত ঘন্টা তো সে নিশ্চয়ই ঘুমিয়েছে। সকাল হবার পর বাকি ন’ দশ ঘন্টায় কী এমন ঘটল যে ফিজু একটা অচেনা ফাঁকা ঘরে গিয়ে কালঘুমে ঘুমিয়ে পড়ল! ভাবলেই রোশনের বুকের ভেতরটা বেবাক ফাঁকা হয়ে যায়, যেন তার হার্ট, লাংস,পাঁজর, কিছুই নেই। নিজের বুক চেপে ধরে রোশন, সেখানে সর্বগ্রাসী শূন্যতার মধ্য দিয়ে কোন দৈবী মায়ায় লাবডুব লাবডুব আওয়াজ ভেসে আসছে তবুও! সন্ধেবেলায় ক্যাম্পাসে তারা পৌঁছনোর পর ভীম আর্মির কমরেডদের সূত্রে রাজশেখরন নামে একটি ছেলে দেখা করতে এল। না, সে এ ব্যাপারে কিছুই জানে না। কারণ ওই সময়ে সে অন্ধ্রে নিজের বাড়ি গিয়েছিল। সে শুধু রোশন যেখানে বলবে সেখানে নিয়ে যেতে পারবে। এত বড় ক্যাম্পাসে নাহলে কোথায় কী আছে, কোনও নবাগতের পক্ষে তা জানা সম্ভব না। এটুকু সাহসও তার হত না, কিন্তু সে খুবই সিনিয়র ফেলো, আর কয়েক মাসের মধ্যেই পাততাড়ি গুটিয়ে বাড়ি ফিরে যাবে। রোশন তাকে বলল,আগে আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবে আন্না? যেখান থেকে প্রথম ডাক্তার গিয়ে মৃতদেহ পরীক্ষা করেছিলেন? তারা বাইকে স্টার্ট দিচ্ছে, এমন সময় পাগলের মত ফতিমা ছুটে এল,- আমাকে না নিয়ে কোথায় যাচ্ছিস বিড্ডা? আমি যাব, আমি যাব। তার মুখের দিকে তাকিয়ে রোশন বুঝল কিছুতেই তাকে ফেলে যাওয়া চলবে না। তাই ফতিমাকে মাঝখানে বসিয়ে ছেলেদুটো দুজন দুদিকে বসল।ক্যাম্পাসের এই পুরনো হাসপাতালটা গেস্ট হাউজের কাছেই। অনেক দূরে কোথায় নাকি আই আই টির জন্য সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল হচ্ছে। এখনও বেশিটা এই হাসপাতালই সামলায়। রাজের বাইকের পেছনে বসে পাঁচ মিনিটে রোশন আর ফতিমা সেখানে পৌঁছে গেল। মূল প্রবেশ পথে ঢুকে বাঁ দিকে যেতে হল, তারপর ডাইনে একটা লম্বা করিডরের শেষে পাশাপাশি আবার অনেকগুলো ঘর। করিডরে লম্বা বেঞ্চে বসা রোগীদের ভিড় ছিল, পোশাক-পরা নার্সরা যাতায়াত করছিল, কথাবার্তা, জুতোর শব্দ, দরজা খোলা বন্ধের ক্যাঁচক্যাঁচ, ওষুধের গন্ধ, বেশ গ্যাঞ্জাম হয়ে ছিল জায়গাটা। রাজশেখরন রোশনের দিকে ফিরে বলল, - সেদিন ছেলেরা প্রথমে ছুটে আউটডোরেই এসেছিল। কিছু ঘটলে ওরা সবসময়ই তাই করে। ওরা তো বুঝতেই পারেনি, শেখ ফয়জুল মরে গেছে, না অজ্ঞান হয়ে রয়েছে। পরে পোস্ট মর্টেম করে জানা গেছে চারদিনের বাসি মরা ছিল। কিন্তু আশ্চর্য হয়েছি এই শুনে যে মৃতদেহ থেকে কোনো গন্ধটন্ধ বেরোচ্ছিল না। এমার্জেন্সি থেকে ডাক্তারকে ওরা হস্টেলের সেই ঘরটায় নিয়ে যায়। - সেই ডাক্তারের আজ ডিউটি আছে তো? আমি তার সঙ্গে কথা বলব। - হ্যাঁ, সেসব খবর আগেই নিয়েছি। আজ ওঁর এখানে নাইট ডিউটি আছে। একটা ভারী কালো কাঠের দরজায় রাজশেখর ঠকঠক করে। তার ওপরে নেমপ্লেটে লেখা ড: ধরিত্রী সান্যাল, এম ডি। ভেতর থেকে নারীকন্ঠে প্রত্যুত্তর আসে, - প্লিজ কাম ইন।একসঙ্গে এত লোককে ঢুকে পড়তে দেখে ডাক্তার-ম্যামের ভ্রূ কুঁচকে যায়,- রোগী ছাড়া আর দুজন বাইরে দাঁড়ান। আমি দরকার বুঝলে ডেকে নেব।রাজশেখর বা রোশন কিছু বলার আগেই ফতিমা হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে, সামনের টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে জড়ানো গলায় ডাক্তারকে নিজের ভাষায় জিজ্ঞাসা করে, - নোডিডিয়া নান্না মাগু? আপনি কি আমার বাছাকে দেখেছিলেন? ডাক্তার হতবাক হয়ে যায়, তারপর ভাষা না বুঝেও কী একটা সন্দেহ তার কপালে ভাঁজ ফেলে। রাজশেখরনের দিকে তাকিয়ে সে ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করে, - এরা কি শেখ ফয়জুলের কেউ হন? রোশন হাত জোড় করে বলে, - হ্যাঁ, ইনি ফয়জুলের মা, আমি বন্ধু। ম্যাম, সেদিন আপনি কী দেখেছিলেন, বলবেন আমাদের? ফতিমার অনবরত ফোঁপানির মধ্যেই ডাক্তার রোশনদের মাথার পেছনের সাদা দেওয়ালে নিজের চোখ গেঁথে রাখে। মুখে বলে,- বসুন আপনারা। ওঁকেও বসান প্লিজ। আমি পুলিশের কাছে যে বয়ান দিয়েছি, আপনাদেরও তাই-ই বলছি। সেদিন জনাদশেক ছেলে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে আউটডোরে ডিউটিরত ড: ধরিত্রীকে এসে একটা খুব খারাপ খবর দেয়। একটি সদ্য জয়েন করা স্কলার হস্টেলের একটি অব্যবহৃত ঘরের মেঝেতে পড়ে রয়েছে, সে মারা গেছে না বেঁচে আছে বোঝা যাচ্ছে না। নাকের নীচে হাত রাখলে শ্বাসপ্রশ্বাস বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু দেখতে ফ্রেশ লাগছে, যেন জোরে ধাক্কা দিলেই হুড়মুড়িয়ে উঠে বসবে। এমার্জেন্সিতে ডিউটি তার, প্রচুর রোগী অপেক্ষা করছে, তার মধ্যে এ কী ঝামেলা !শরদিন্দু চ্যাটার্জি তার জুনিয়র। বললেই চলে যেত। কিন্তু ধরিত্রী নিজেই যাবে ঠিক করল। গত বছরও এইসময় ক্যাম্পাসে একটা আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছিল। পুলিশের কাছে তখনকার ডাক্তার যে বয়ান দিয়েছিল, তাতে অনেক অসঙ্গতি ছিল। তাই নিয়ে সে কী ঝামেলা! ধরিত্রী ঠিক করল সে নিজেই যাবে। ছেলেদের কাছ থেকে ঠিকানাটা ভালো করে জেনে নিয়ে বলল, - তোমরা এগোও। আমি আসছি। জিমের সামনে দিয়ে আস্তে আস্তে ড্রাইভ করে এগোচ্ছিল ধরিত্রী, এই রাস্তাটায় বড় বড় সব স্পিড ব্রেকার বিছিয়ে রাখা আছে। উপায় নেই, জিম করে সব আলালের ঘরের দুলালরা সাঁ করে বাইক ছোটান সুইমিং পুলের দিকে। সে সময় তাদের গায়ে এত পুলক লেগে থাকে যে চক্ষে ঘোর ঘনিয়ে কে যে কোথায় বাইক নিয়ে পপাত চ মমার চ হবেন, কেউ বলতে পারে না। এই জেনারেশনটাকে সে ঠিক বুঝতে পারে না। কখনও মনে হয় ওরাই ভালো, কেমন স্পষ্ট ভাবে নিজেদের চাহিদার জানান দিতে পারে। পোষালে থাক, নইলে কেটে পড়। আবার কখনও মনে হয়, না: বড্ড আত্মকেন্দ্রিক! নিজেদের নিয়েই মত্ত। এই যে ষোল হাজার ছেলেমেয়ে নিয়ে একটা এতবড় ক্যাম্পাস, এদের মধ্যে ক'জন সমাজের কথা ভাবে, দেশের জন্য মাথা ঘামায়। তবে কিনা, একটু দু:খের হাসি হাসে ধরিত্রী, আমরাই কি দায়ী নই এ জন্য? স্বার্থমগ্নতা কি আমরাই যত্ন করে শেখানোর সিলেবাসে এক নম্বরে রাখিনি? সেখানে একটু আঘাত লাগলেই আত্মহত্যা, নয়ত অন্যকে আঘাত করা। প্রত্যেক বছর ক্যাম্পাসে একাধিক আত্মহত্যা! আর মারামারি তো লেগেই আছে। হাতাহাতি থেকে ধারাল অস্ত্র নিয়ে চোরাগোপ্তা আঘাত করা, সবই ঘটে। তবে প্রশাসনের ভূমিকাও খুব হতাশাজনক। যাই-ই ঘটুক না কেন, সবার আগে প্রতিষ্ঠানের সুনাম, এই নীতিতে চললে, কারও প্রতি সুবিচার করাই সম্ভব নয় ! ছেলেটি যে ভাবে মেঝেয় এলিয়ে পড়েছিল, দূর থেকে দেখেই ধরিত্রীর অভিজ্ঞ চোখ বুঝল, এ মৃত। তাকে লিফটের বাইরে আসতে দেখেই জমায়েতটা সরে সরে পথ করে দিল। ছেলেটার নাড়ি দেখবে বলে হাতটা তুলতেই, কী একটা অনুভূতি তাকে বেদম অস্বস্তিতে ফেলে দিল। অনেক ভেবে ধরিত্রী বুঝতে পারে তার অস্বস্তি হচ্ছে মৃত ছেলেটির ত্বকের বিবর্ণতা দেখে ! অনেক আগে কেউ মারা গেলে তার ত্বক যেমন বেরঙ, শুকনো খড়খড়ে হয়ে যায়, এরও তেমনি। কিন্তু আর সবই অল্পবিস্তর ঠিকঠাক! ভালো করে খুঁটিয়ে দেখে ধরিত্রী। আধবোজা চোখদুটো নিয়ে মুখ মাথা একদিকে হেলে পড়ছে। হাত পাগুলো এমন ছেতরানো, দেখলে মনে হচ্ছে গামছা নিংড়োবার মত ওগুলো থেকে কেউ নিংড়ে নিয়েছে মনুষ্যদেহের স্বাভাবিক শক্তির শেষ বিন্দুটুকু। কবে এর মৃত্যু হয়েছে? কতদিন হল ও এই ধুলোভরা মেঝের ওপর পড়ে আছে? নাড়ি দেখা শেষ করে মুখ তুলল ধরিত্রী, স্টেথো বার করতে করতে ছেলেগুলোকে জিজ্ঞাসা করল, - পুলিশে খবর দিয়েছ?- হ্যা ম্যাম, পুলিশ আসছে। আরও দু একটি কথা চালাচালিতে সে বুঝল, কেউই চিনত না ছেলেটিকে, ও যে এইখানে পড়ে আছে সে খবরও কারও কাছে ছিল না। ঘরের দরজাটা ভেজানো ছিল, আজ ছুটির দিনে এই ফ্লোরের কয়েকজন মিলে একসঙ্গে বেরচ্ছিল। হয়ত ফিল্ম দেখবে কিম্বা রেস্টুরেন্টে খেয়ে মুখ বদলাবে। ছোট লিফট, তাই লিফটে কে বা কারা আগে যাবে সেই নিয়ে নিজেদের মধ্যে মজার হুটোপুটি বেঁধে যায়। ধাক্কাধাক্কি করবার সময় একজনের কনুই লেগে হঠাৎ লিফটের লাগোয়া এই ঘরের দরজাটা খুলে যায়। কেউ থাকতো না বলে ওটার কোনো খবর রাখত না কেউ। জানালাবন্ধ ঘরের আধো অন্ধকারে কেউ মাল খেয়ে বেহোঁশ হয়ে শুয়ে আছে, এইরকম ভেবেছিল ওরা। তারপর অনেক ডাকাডাকি করে সন্দেহ হওয়ায় কয়েকজন সময় নষ্ট না করে ডাক্তার ডাকতে হাসপাতালে চলে যায়। এর মধ্যেই পুলিশ চলে আসে। ধরিত্রীকে ওসি চেনে। বছর বছর আত্মহত্যার কেস ডিল করতে হলে পুলিশ, উকিল আর ডাক্তারে মুখ শোঁকাশুকি না হয়ে উপায় থাকে না। - আরেকটা সুইসাইড? ওসির সর্দিবসা গলা কানে আসে ধরিত্রীর, - গায়ে জ্বর নিয়ে আসতে হল ম্যাডাম। এ তো দেখি আত্মহত্যা করেই যদুবংশ ধ্বংস হয়ে যাবে ! তার উত্তরের অপেক্ষা না করেই ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে পুলিশবাহিনী। পটাপট সব আলোগুলো জ্বেলে দেয়। কে একজন ভিড়ের মধ্য থেকে বলে ওঠে,- শেখ ফয়জুল, রিসার্চ স্কলার, লালা লাজপত রায় হস্টেল। রুম নাম্বার টুয়েন্টি টু। আ নিউ কামার টু হিজলি ক্যাম্পাস।- কে রে, কে? কে বলল কথাটা? ওসি আবার ঘরের ভেতর থেকে বার হয়ে আসে। রুল উঁচিয়ে ধরে ক্রমশ ফুলে ওঠা জমায়েতের একের পর এক ছেলের দিকে,- আপনি, আপনি বললেন? নাকি আপনি? কে কী জানেন বলুন, তাতে আমাদের ইনভেস্টিগেশনের সুবিধে হবে ! কিন্তু নিরেট ভিড়টা থেকে একটা টুঁ শব্দও উঠে আসে না। একটা জমাট ধরা শ্বাসপ্রশ্বাসের ডেলা যেন ওটা। প্রাণ আছে, কিন্তু সুপ্ত, শ্বাসপ্রশ্বাস নেওয়া ছাড়া প্রাণের আর কোনও লক্ষণই দেখায় না ভিড়টা। শুধু আলো পিছলে যায় সুন্দর প্রসাধিত বুদ্ধিদীপ্ত মুখগুলোর ওপরে। বড্ড চকচকে, বড় বেশি উজ্জ্বল যেন ! কৃত্রিম উজ্জ্বলতা। ধরিত্রীর মনে পড়ে ক্যাম্পাসের বাইরে দেওয়াল ঘেঁষে সারি সারি গজিয়ে উঠেছে ইউনিসেক্স পার্লার ! ছাত্রদের কাছ থেকে কোন সাড়া না পেয়ে এবার পুলিশ স্ট্রেচারে লাশটা তোলার তোড়জোড় করল। দূর থেকে ছেলেটিকে যেমন নেতিয়ে পড়ে আছে বলে মন হচ্ছিল, স্ট্রেচারে তোলার সময় ধরনধারণ দেখে সেই ভাবটা বেশ কম বলে মনে হল ধরিত্রীর। বেশ শক্ত যেন দেহখানা। কিন্তু তাই-ই বা কী করে হবে, রাইগর মর্টিসের লক্ষণ কোথায় ! দেহে পচন ধরেনি, দুর্গন্ধ নেই! ধরিত্রী খুব অবাক হচ্ছিল, কিন্তু ব্যাপারটা এখন তার হাতের বাইরে। লাশ চলে যাবে সোজা মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজের মর্গে। সেখানেই পোস্ট মর্টেম হবে। দেখা যাক, কী রিপোর্ট আসে! ধরিত্রী চলে যাবে বলে পেছন ফিরেছে, হঠাৎ ঠনঠন করে কিছু গড়িয়ে যাবার শব্দ। এক পুলিশের পায়ে লেগে কৌটো মতো কিছু একটা গড়িয়ে গেল ঘরের ভেতরে টয়লেটের দরজার দিকে। আর একজন সেটা কুড়িয়ে নিল। মনে হচ্ছে কোন ওষুধের কৌটো, বেশ বড়সড় সাইজের। ওসি নাকের ডগায় চশমা টেনে গায়ের লেখা পড়ার চেষ্টা করে কিছু বুঝতে না পেরে ধরিত্রীকে বলল,- ম্যাডাম, দেখুন না একটু, এটা কিসের ওষুধ! কৌটোটা হাতে নিয়ে চমকে উঠল ধরিত্রী। এমপ্লুরা। মাংস সংরক্ষণে এর জুড়ি নেই। যে কোনো রকম মাংসে এই ওষুধ মাখালে সেটা অনেক সময় ধরে তাজা থাকে, গন্ধ ছাড়ে না, খুব শক্ত হয়ে যায় না, ছোট্ট পাখি তিতির থেকে মানুষের…হ্যাঁ মানুষেরও তো…! আরে এ ওষুধ এখানে কেন! ধরিত্রীর পা থেকে মাথা অবধি বিদ্যুৎচমকের মতো কী যেন খেলে গেল! লিফটে নামতে নামতে তার কেবলই মনে হচ্ছিল লাশটি এতো গন্ধ ও পচনহীন কেন সে রহস্য যেন সে উদঘাটন করে ফেলেছে ! সারা রাত ধরে নির্ঘুম বসে থাকতে থাকতে অস্থির হয়ে পড়ল রোশন। ডিরেক্টর এখানে নেই, আগামীকাল তাদের ডিনের সঙ্গে দেখা করবার কথা। পাশের ঘরে ফতিমা আন্টিকে কড়া ঘুমের ডোজ দিতে হয়েছে। এখানকার ডাক্তার-ম্যাডামই দিল নিজে থেকে, ফতিমার মুখচোখ দেখে। রোশনকে গলা নামিয়ে বলল, - আমিও তো মা। নিজের জোয়ান ছেলে মরে গেলে মনের ভেতরে কী হয় তা ভালই বুঝি। এই ওষুধটা রাখ। রাতের খাবারের আধ ঘন্টা আগে এটা ওঁকে খাইয়ে দিও। গোটা হিজলি ক্যাম্পাসে এই ডাক্তার দিদিমণিই একমাত্র মানুষ যে ফতিমার প্রতি তবু কিছু সহানুভূতি দেখিয়েছিল। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে রাজশেখরণ ওদের নিয়ে গেল থানায়। আগেই জানান হয়েছিল, মৃত ছাত্রের মা দেখা করবে। ওসি তাদের বেশ খাতির করে বসাল, কিছুক্ষণ ফতিমাকে ‘মা’ বলে সম্বোধন করে খুব মিষ্টি ব্যবহার করল, তারপর নিরীহ হরিণের চামড়ায় ঢাকা সিংহের আসল চেহারা দ্রুত বেরিয়ে পড়ল। দোষের মধ্যে ফতিমা তার ছেলের মৃতদেহের ছবি দেখতে চেয়েছিল, - আমার ফিজুকে দেখতে চাই। কেমন ভাবে পড়েছিল আমার মাগু, আমার কুসু, দেখাও অফিসার, আমাকে দেখাও! দোভাষীর কাজ করতে করতে রোশন দেখছিল, ফতিমা আন্টির অস্থিরতা যতই বাড়ছে, ওসির মুখ ততই কঠোর হয়ে উঠছে। একসময় লোকটা ফতিমার মুখের ওপর বলে বসল,- লাশের কোনো ছবি আমাদের কাছে নেই।তার মানে? এই রকম কেসে ছবি তুলে সংরক্ষণ করে রাখা তো ম্যান্ডেটরি। রোশন দোভাষির ভূমিকা ছেড়ে এখন সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ। - হ্যাঁ, তোলা হয়েছিল। কিন্তু আমরা ডিলিট করে দিয়েছি। আমাদের তদন্তের কাজ মিটে গেছে। ওসব ছবির আর কোনো মূল্য নেই।রোশন খুব অবাক হয়ে ওসির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। ফতিমা কিছুই বুঝতে না পেরে অঝোরে কেঁদে চলে। ওসির রাগ ক্রমশ চড়ছিল, সে গজগজ করতে করতে বলে,- এইরকম কেস মানে কী রকম কেস, হ্যাঁ? এটা একটা প্লেন এন্ড সিম্পল সুইসাইড কেস। - তাহলে পোস্টমর্টেম রিপোর্ট ইনকনক্লুসিভ রইল কেন? সেখানেই তো বলা থাকত ফয়জুল আত্মহত্যা করেছে।উত্তেজনায় ওসি চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ে,- আপনাকে তো পড়াশোনা জানা বলেই মনে হচ্ছে। সারকামস্ট্যানশিয়াল এভিডেন্স বলে কিছু আছে সেটা জানেন তো। শেখ ফয়জুলের কবজিতে ব্লেড দিয়ে চেরার দাগ ছিল, জানতেন এ কথাটা? এখানে আসার পর থেকেই ওর ধরনধারন দেখে রুমমেটদের সন্দেহ হয়েছিল, ও হয় ড্রাগ এডিক্ট, নয় ডিপ্রেশনের রোগী। ও আত্মহত্যাই করেছে। ফতিমা এই দুজনের মধ্যে কথাবার্তার কিছুই বুঝতে পারছিল না, কান্না থামিয়ে একবার ওসি, একবার রোশনের মুখের দিকে তাকাচ্ছিল। রোশনও এবার চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে, ওসির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। এ সেই দৃষ্টি যা তাকে কেউ হেই চামারের ব্যাটা, হেই মাদিগার ব্যাটা বলে অপমান করলে, তার দুচোখ ভেদ করে বেরিয়ে আসত। গলা ওঠায় না সে, কিন্তু খুব প্রত্যয়ী শোনায় তার কন্ঠ, - স্যার, আমরা পঁচিশ বছর ধরে পরস্পরের বেস্ট ফ্রেন্ড ছিলাম। আমি জানি, ফয়জুল কোনওদিন ড্রাগ ছুঁয়ে দেখেনি আর ডিপ্রেশনেও সে ভোগেনি। প্লেন এন্ড সিম্পল তাকে কেউ মার্ডার করেছে। আমরা হাইকোর্টে কেস করব। ফিজুর দেহ কবর থেকে তুলে আবার পোস্ট মর্টেম করাব। দেখব কী করে তদন্ত শেষ বলে আপনারা এভিডেন্স নষ্ট করে ফেলেন। ওসি থতমত খেয়ে যায়। তারপর নিজেকে ফিরে পেয়ে বলে, - প্রমাণ করুন। মুখে বললে তো হবে না। আমরা ইনভেস্টিগেশন করে যা পেয়েছি, তার ভিত্তিতে বলছি এটা আত্মহত্যার কেস। আমার কথা মানবেন না যখন, তখন আপনারা আসুন। আমার যা বলার ছিল বলা হয়ে গেছে। তবে যাবার আগে এই কাগজটায় সই করে যাবেন দুজনেই। আমাদের কথাবার্তার সারাংশ এখানে লেখা আছে।রোশন কাগজটা টেনে নিয়ে পড়তে গিয়ে দারুণ চমকে উঠল। যতদূর সম্ভব এটা বাংলায় লেখা। ওসির মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল, লোকটা হাসি হাসি মুখে তাদের দিকে তাকিয়ে আছে। ভাবটা এমন, যে সে যেন বলছে, কী কেমন দিলাম? হাতের উদ্যত পেন নামিয়ে রেখে সই না করেই ফতিমাকে নিয়ে রোশন বাইরে চলে আসে। গোটা কথাবার্তাই সে তার মোবাইলে গোপনে রেকর্ড করে নিয়েছে।” সূত্রঃ "ফৈজান আহমেদ আত্মহত্যা করেন নি", অমিতাভ চক্রবর্ত্তী, গুরুচণ্ডা৯। ১৫ জুন ২০২৪IIT-Kharagpur student’s murder: ‘How could institute and police cover up so much,’ asks Faizan’s mother, Sukrita Baruah, Jun 15, 2024, The Indian Expressসদ্য প্রকাশিত রসিকার ছেলে উপন্যাস নিয়ে দেবকুমার চক্রবর্তীর আলোচনা। রসিকার ছেলেপ্রতিভা সরকার। প্রকাশক: গুরুচণ্ডা৯মূল্য—১৫০ টাকা। বাড়িতে বসে বইটি পেতে হোয়াটসঅ্যাপে বা ফোনে অর্ডার করুন +919330308043 নম্বরে।মহারাজ ছনেন্দ্রনাথ ও বিদেশি চকলেটের বাক্স - রমিত চট্টোপাধ্যায় | অলংকরণ: রমিত চট্টোপাধ্যায়মহারাজ ছনেন্দ্রনাথ ওরফে ছেনু তখন থেকে অপেক্ষা করে রয়েছে কখন চিঠিটা সবার পড়া শেষ হবে। বাড়িতে কারুর চিঠি আসা মানেই ওর খুব মজা, আরেকটা ডাকটিকিট এসে খাতায় জমা হবে। খাতায় ডাকটিকিটটা সাঁটার কায়দাটা একটু খটোমটো। ওকে তেতলার দাদাই পুরোটা শিখিয়েছিল। প্রথমে খামের পিছনদিকটা অল্প জল দিয়ে ভিজিয়ে তারপর আলতো করে ব্লেড ঘষে ঘষে খুউব সাবধানে স্ট্যাম্পটা তুলে শুকিয়ে নিতে হবে। এরপর পাতলা একফালি সেলোফেন পেপার আধভাঁজ করে স্ট্যাম্পের পিছনে অল্প একটুকুনি আঠা লাগিয়ে সেলোফেন পেপারের আরেকটা দিক আলতো করে ধরে খাতায় চিপকে দিতে হবে। এই করে করে ছেনুর খাতায় এত্তোগুলো ডাকটিকিট জমে গেছে।আজকে সকালে তেতলার পিসিমার কাছে যে চিঠিটা এল, দাদা মানে পিসিমার ছেলে অনেকক্ষণ ধরে পিসিমাকে পড়ে পড়ে শোনাচ্ছে। ছেনু গিয়ে দু'বার দরজার সামনে থেকে ঘুরেও এল, কত লম্বা চিঠি রে বাবা! শেষে আর থাকতে না পেরে ছেনু গিয়ে পিসিমাকে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করেই ফেলল, কার চিঠি গো? দেখা গেল অদ্ভুত ব্যাপার, পিসিমা হাসছে, অথচ চোখের কোণে জল, পিসিমা হেসে বলল, কে আসছে জানিস? কান্টু আসছে রে কান্টু, তোর কান্টু দাদা। এদ্দিন পর ও আসছে, শুনে বিশ্বাসই করতে পারছি না, তাই তো বারবার করে শুনছি।ছেনু ছোট্ট থেকে পিসিমার কাছে কান্টুদার অনেক গল্প শুনেছে, কিন্তু কোনোদিন কান্টুদাকে চোখে দেখেনি আজ পর্যন্ত। অবশ্য দেখবেই বা কি করে, ছেনুর জন্মের আগেই তো পিসিমার বড় ছেলে কান্টুদা সেই সাত সমুদ্দুর তেরো নদী পার করে কি একটা দেশ আছে, কানাডা না কি নাম, সেইখানে চলে গিয়েছিল। সেই থেকে সেখানেই থাকে আর মাঝে মধ্যে চিঠি লিখে খবরাখবর জানায়। শুরুর দিকে বাংলায় লিখত বটে কিন্তু পরে কি জানি কেন শুধু ইংরেজিতেই চিঠি পাঠায়, তাই অন্যরা পিসিমাকে তর্জমা করে পড়ে পড়ে শোনায় কি লিখেছে।পিসিমার মুখেই ছেনু শুনেছে, কান্টুদার নাকি ছোটো থেকেই খুব বিদেশ যাওয়ার শখ, বড় হয়ে কলকাতার চাকরিতে মন টিঁকছিল না, কান্টুদা শেষমেশ ঠিক করল, না, আর কোলকাতায় না, খাস বিলেতেই যেতে হবে। যেমন কথা তেমনি কাজ, পরিবারের কিছু টাকার সাথে, নানা আত্মীয়স্বজনদের থেকে আরো কিছু টাকা ধার নিয়ে একসাথে জমিয়ে জাহাজে চেপে সোজা রওনা দিল বিলেতে। লন্ডনে নেমে নানা জায়গায় ঘুরে তেমন কিছু সুবিধা করতে না পেরে মুখ ভার করে বসেছিল, এমন সময় কার কাছে শুনেছে, নানা জায়গার লোক এসে নাকি লন্ডনে প্রচুর ভিড় হয়ে গেছে আর ওদিকে আরও দূরে কানাডায় নাকি প্রচুর কাজের লোকের দরকার। কান্টুদা শুনেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল, তাহলে এখানে বসে থেকে লাভ নেই, চলো কানাডা! আবার লন্ডন থেকে জাহাজে চেপে পাড়ি দিল আটলান্টিক মহাসাগর পেরিয়ে কানাডায়।সেখানে তো ভীষন ঠাণ্ডা, কান্টুদার সাথে গরম জামা বলতে একটাই কোট ছিল। যাই হোক রাস্তা থেকে আরেকটা ওভারকোট কেনার পর খোঁজখবর করে কম পয়সায় একটা বাড়িও ভাড়া করা হল। সেই কোট পরে কান্টুদা এদিক ওদিক কাজের খোঁজে যায়, কিন্তু যে সব কাজ জোটে সেসব মনে ধরে না পুরসভার চাকরির পাশাপাশি যাদবপুরের নাইট থেকে ইন্জিনিয়ারিং পাশ করা কান্টুদার। সারাদিনে খুব সামান্য কিছুই পেটে পড়ে, সারাদিন ঘুরে ক্লান্ত হয়ে রাত্রে ঘরে ফিরে ঘুমিয়ে পড়ে। নতুন দেশে গিয়ে তো কিছুই ঠাহর করতে পারছে না, খাবার দাবার খেতে, টুকিটাকি জিনিসপত্র কিনতেই জমা টাকা হুহু করে খরচ হয়ে যাচ্ছে! দেখতে দেখতে দুটো মাস কেটে গেল, প্রথম মাসের বাড়িভাড়া তো শুরুতেই দিয়ে দিয়েছিল, বাড়িওলা এবার এসে পরের মাসের ভাড়া চাইছে। কান্টুদা অনেক করে বোঝায়, ক'টা দিন দাঁড়াও, আমি চাকরি পেয়েই ভাড়া মিটিয়ে দেব। বুঝিয়ে সুঝিয়ে দিন দশেক কোনোক্রমে আটকে রাখা গেছিল, কিন্তু কপালের লেখা কে আটকাবে! একদিন খুব বৃষ্টি পড়ছে তার মধ্যে বাড়িওলা খুব চিৎকার চেঁচামেচি করে কান্টুদাকে বাক্সপ্যাঁটরা সমেত বাড়ি থেকে বের করে দিল। কান্টু দা কি আর করে, কোটখানা গায়ে চাপিয়ে বাক্স হাতে করে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে রাস্তায় অন্য একটা বাড়ির নীচে একটু আড়াল মতো পেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আড়াল পেলেও, এমন জোর বৃষ্টি শুরু হল যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাকভেজা ভিজে গেল।এমনি সময় হঠাৎ একটা মেয়ে পাশের বাড়ির জানলা থেকে মুখ বাড়িয়ে, কান্টুদাকে দেখতে পেয়ে বলল, ওখানে দাঁড়িয়ে আছো কেন? ভিজে যাবে তো! কে তুমি? কান্টুদা কি আর করে, মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, ইন্ডিয়া থেকে এসেছি চাকরি করতে, একটু বিপদে পড়েছি, বৃষ্টিটা ধরলেই চলে যাব।তাতে মেয়েটা বলে, ওখানে দাঁড়িয়ে থেকো না, বৃষ্টির মধ্যে ঠাণ্ডায় জমে যাবে, দরজা খুলে দিচ্ছি, ওপরে এসে বসো। তারপর গরম চা খেতে খেতে মেয়েটা কান্টুদার মুখ থেকে গোটা ঘটনা শুনল। নরম মনের মেয়ে, শুনে টুনে বলল, এটা আমার দিদার বাড়ি, আমি দিদার সঙ্গেই থাকি। তোমার তো থাকার কোনও জায়গা নেই, এক কাজ করো, যদ্দিন না চাকরি পাচ্ছো এখানে আমাদের সাথেই থাকো, আমি দিদার সাথে কথা বলছি। আপাতত জামাকাপড় বদলিয়ে শুকনো কিছু পরে নাও।পিসিমা যখন গল্পটা ছেনুকে বলেছিল, ছেনু তো শুনে অবাক, এতো দারুণ ব্যাপার! কান্টুদাকে আর ভিজতে হল না, আচ্ছা ওদিন যে অত করে সাহায্য করল, সেই মেয়েটা কে গো? পিসিমা বলেছিল, দাঁড়া দেখাচ্ছি, বলে কোন একটা ডায়েরির মধ্যে থেকে একটা টুকটকে ফর্সা গোলগাল মেয়ের ছবি বের করে ছেনুর হাতে দিয়ে বলল, এই দ্যাখ। ছেনু হাতে নিয়ে সেই মেমসাহেবের ছবি দেখে অবাক হয়ে বলল, সেই ছবি তুমি কী করে পেলে? পিসিমা বলে, ওমা পাবো না কেন? কান্টুই তো পাঠিয়েছে। ভালো করে দেখে রাখ, এই হল তোর বৌদি, জুলি বৌদি। ওখানে চাকরি বাকরি জুটিয়ে সেই জুলির সাথেই তো পরে ওর বিয়ে হয়েছে।তারপর অনেক দিন কেটে গেছে, কান্টুদা পাকাপাকিভাবে কানাডাতেই থাকে আর মাঝে মাঝে চিঠিতে খবরাখবর পাঠায়, তেমনই এক চিঠি আজ সকালে এসেছিল। তাতে কান্টুদা জানিয়েছে, সে জুলি বৌদি আর বাচ্ছাদের নিয়ে এবার কোলকাতায় আসছে সবার সাথে দেখা করতে। সেই কথা শুনে তো সারা বাড়িতে হইহই পড়ে গেল। বিদেশের অতিথি তার ওপরে আবার বাড়ির বউ! তার সামনে তো বাড়ির একটা প্রেস্টিজ আছে নাকি? সাথে সাথে রংমিস্তিরির কাছে খবর গেল, সারা বাড়ি চুনকাম করা হবে। তিন বোতল অ্যাসিড কিনে আনা হল, পুরো বাথরুম সেই দিয়ে পরিষ্কার করা হবে ঝকঝকে তকতকে করে। খাবার পরিবেশনের জন্য এল চকচকে নতুন কাঁসার থালা-বাটি-গ্লাস। আরও হ্যানো ত্যানো নানান নতুন নতুন জিনিস কেনার লিস্টি তৈরি হল। মোটকথা যেভাবেই হোক শেয়ালদার সম্মান যাতে বজায় থাকে সেই চেষ্টার কোনও ত্রুটি রাখা যাবে না।এই সব দৌড়াদৌড়ির মধ্যেই টুকটুক করে কান্টুদাদের আগমনের দিন এসে পড়ল। পিসেমশাই আর দাদা মিলে সেই দমদম এয়ারপোর্ট থেকে আনতে যাবে, সকাল থেকে তার প্রস্তুতি চলছে। ছেলের জন্য নানান রকম রান্না করা চলছে পিসেমশাযের চিন্তা কানাডার বৌমা প্রথম দেখায় প্রণাম করবে, হ্যান্ডশেক করার জন্য হাত বাড়িয়ে দেবে, নাকি আবার ওদেশের রীতি মেনে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরবে! তেতলার দাদা জামা প্যান্ট পরে রেডি, বাবাকে বোঝাচ্ছে, আরে দাদা তো আছে, তুমি ঘাবড়াচ্ছ কেন। ওদিকে আবার রান্নাঘর জুড়েও প্রস্তুতি তুঙ্গে। ছেলের জন্য নানান রকম রান্না করা চলছে, পঞ্চব্যঞ্জন দিয়ে আপ্যায়ন না করলে চলবে! ওদিকে আবার চিন্তা পাঁঠার মাংস তো ঠিক আছে কিন্তু কানাডার লোকে পাকা রুইয়ের কালিয়া, আলু পটলের ডালনা, উচ্ছে ভাজা, বেগুন ভাজা এসব ঠিকমতো খাবে তো? আসলে এগুলো কান্টুদার খুব প্রিয় পদ ছিল তো।বাড়ির নিচে দুটো ট্যাক্সির হর্ন শোনা যেতেই বাড়িজুড়ে যেন হাজার ওয়াটের বাল্ব জ্বলে উঠল। কেউ রান্নাঘরে ছুটছে, কেউ গ্লাসে করে জল নিয়ে আসছে আর বাকিরা সবাই মিলে সিঁড়ির দুধারে ভিড় করে দাঁড়িয়ে উঁকি ঝুঁকি মারছে। ছেনুও মনে মনে উত্তেজনায় ফুটছে, এতদিনের গপ্পের চরিত্রদের সাথে আজ দেখা হবে! ওরা সমস্ত বাক্স-প্যাঁটরা নিয়ে উঠতেই সটান বরণডালা হাতে পিসিমার মুখোমুখি। বিয়ে অনেকদিন হতে পারে, কিন্তু এবাড়িতে তো প্রথমবার, বরণ না করলে চলবে! সাথে চলল বাড়ির বাকি মহিলাদের সমবেত উলুধ্বনি।কিন্তু এদিকে মহারাজ ছনেন্দ্রনাথের মন ভেঙে গেছে, ছবির সাথে বাস্তবের বিন্দুমাত্র যে মিল নেই! ছবিতে যে গুবলু গাবলু মিষ্টি দেখতে বিদেশি মেয়েটাকে দেখেছিল, সে কই? এ তো বেশ রোগা, চোখ বসে গেছে, আর গরমের দেশে এসে ঘেমেনেয়ে একসা। সাথে আবার দুটো বাচ্চা ছেলেও আছে, ছেনুর থেকে বয়সে বোধহয় একটু ছোটই হবে কিন্তু দেখতে পুরোদস্তুর সাহেব। তারা কী যে বলছে ছেনু কিছুই বুঝতে পারছে না, তবে দেখল কান্টুদা কিছু একটা বলতেই টুক করে নিচু হয়ে পিসিমাকে প্রণাম করে ফেলল আর মুখে তাদের সারাক্ষণ হাসি লেগেই রয়েছে।বৌদিও ঢুকেই হাতজোড় করে সবাইকে নমস্কার করল, যা দেখে সবাই ইমপ্রেসড। প্রণাম টনামের পালা চুকিয়ে মালপত্র নিয়ে বাড়িতে ঢুকতে ঢুকতে পিছনে দেখা গেল বিশাল বিশাল দুটো সুটকেস নিয়ে দাদা আর পিসেমশাই আসছে, পিসেমশাইয়ের মুখটা বেশ হাসি হাসি। আবার তার পিছনে দেখা গেল ছেনুর বড়দাও চলে এসেছে কান্টুদাদের জন্য প্রচুর সন্দেশ, রসগোল্লা, জিলিপি, সিঙাড়া, চমচম বাক্সভর্তি করে নিয়ে। কখন যে টুক করে এসব আনতে চলে গিয়েছিল, ছেনু টেরই পায়নি।তা সেসব সাজিয়ে দেওয়া হল প্লেটে করে। পিসেমশাই আবার বকাবকি করছে বড়দাকে, এত বেশি মিষ্টি টিষ্টি আনার জন্য, পিসেমশাইয়ের ধারণা সিঙাড়া, জিলিপি, এসব আনা উচিৎই হয়নি, এসব আনহেলদি খাবার ওরা ছুঁয়েও দেখবে না। কিন্তু কি আশ্চর্য! ওই বাচ্চা দুটো প্লেটের সবকিছু নেড়েচেড়ে দেখে প্রথমে সিঙাড়াটা ভেঙেই মুখে দিল। নতুন রকমের খাবার খেয়ে মুখ খুশিতে আরো উজ্জ্বল হয়ে বলে উঠল, বলে, ভেরি ভেরি টেস্টি, আই লাইক ইট! তা শুনে বড়দার আনন্দ আর দেখে কে! কান্টুদা ও একটু নিশ্চিন্ত হলো ওদের ভালো লেগেছে দেখে। শেষমেশ দেখা গেল, এখানকার খাবার দাবার সবারই পছন্দ হয়েছে, সাথে চামচ দিয়ে জিলিপি আর সিঙাড়া খাওয়ার কায়দা দেখে বাড়ির লোকেরা একটু মুখ টিপে হেসেও নিল।জলখাবার পর্ব মিটতে ওদের খাটে নিয়ে গিয়ে বসানো হল একটু বিশ্রাম নেওয়ার জন্য, এতটা পথ জার্নি করে এসেছে। দুটো বাচ্চার নামও জানা গেল, পিটার আর ম্যাক্স। পদবি অবশ্য ব্যানার্জি। তো খাওয়া দাওয়ার পর পিটারের বড় বাইরে পেয়েছে, দাদা দেখিয়ে দিল বাথরুম- ওই যে বারান্দার শেষ প্রান্তে। যাক, এই মুহূর্তের জন্যই বাথরুম ভালো করে চুনকাম করিয়ে অ্যাসিড ঢেলে খুবসে পরিষ্কার করা হয়েছে, অবশ্য তাতেও একটা খিঁচ রয়েই গেছে। এই বাড়ির বাথরুমে তো আর ইউরোপিয়ান কমোড নেই, পা ভাঁজ করা দেশি প্যান, সেটায় বসতে পারবে কিনা চিন্তার বিষয়। তবে দেখা গেল বিশেষ বেগ মানুষকে প্যান আর কমোডের পার্থক্য নিয়ে মাথা ঘামাতে দেয় না, ও দিব্যি ভালো ছেলের মতো কাজকর্ম সেরে ভেতরে না পেয়ে, বাইরে মাথা বাড়িয়ে টয়লেট পেপার চাইছে। তারপর দাদা গিয়ে বোঝাল, টয়লেট পেপারের কোনো ব্যবস্থা নেই, জলেই ধুতে হবে। ছেনু দেখল সে পড়েছে ভারি মুশকিলে, অবশেষে কান্টুদা ভিতরে গিয়ে ব্যাপারটা সামাল দেয়। এখানকার কায়দা দেখে বাচ্ছাটা তো অবাক! তবে ভালো ভাবেই মানিয়ে নিয়েছে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে।এরমধ্যে পিসেমশাই গেলেন রান্নাঘরে ব্যস্ত পিসিমাকে ডাকতে, চলো চলো, রান্না তো হয়েই এসেছে প্রায়, এবার একটু ধাতস্থ হয়ে ছেলের সাথে বসে দুটো কথা বলো। একবার দেখো ছেলে কিরকম ফুল সায়েব হয়ে গেছে, চোস্ত ইংরেজিতে কথা বলছে, উফ্, শুনেও গর্ব হয়! পিসিমা হাতের কাজ সামলে ভীষণ উজ্জ্বল মুখ নিয়ে ঘরে গিয়ে বসলেন, কতো বড়ো হয়ে গেছিস রে, আসতে কষ্ট হয়নি তো?কান্টুদা বলে, নো নো নট অ্যাট অল। হাউ আর ইয়ু?শুনেই পিসিমা ভেবলে গেলেন, বলে কি? তারপর উনি যাই বলছেন কান্টুদা উত্তর দিচ্ছে ইংরেজিতে। আর পিসিমা আরো ঘাবড়ে যাচ্ছেন। শেষে পিসেমশাইকে হাঁক পাড়লেন, ওগো শুনছ, এসব কী বিড়বিড় করছে গো, ছেলে কি পাগল হয়ে গেল!অবস্থা বেগতিক দেখে কান্টুদা বলে উঠল, নো নো, আয়াম ফাইন। জাস্ট ফরগট হাউ টু টক ইন বেঙ্গলি, বাট আই আন্ডারস্ট্যান্ড ইয়োর ওয়ার্ডস পারফেক্টলি। পিসেমশাই তখন এসে পড়েছিলেন, পুরো ঘটনাটা পিসিমাকে বোঝাতে, পিসিমার চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়তে লাগল। ছেনু পাশ থেকে ব্যাপারটা পুরো দেখছিল, এতক্ষণ কান্টুদা কী যে বলছিল সেও একবর্ণ বুঝতে পারেনি, কিন্তু পিসিমাকে কাঁদতে দেখে আর থাকতে পারলনা। দাদাকে জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে গো, পিসিমা কাঁদছে কেন! কান্টু দাদা কি পিসিমাকে বকেছে? দাদা আর পিসেমশাই ইংরেজি ভালোই বুঝত। দাদাই গোটা ঘটনাটা ছেনুকে বুঝিয়ে বলল, কান্টুদা আর বাংলায় কথা বলতে পারছেনা বলে পিসিমা খুব দুঃখ পেয়েছে।ব্যাপারটা শুনেও ছেনুও মনে খুব কষ্ট পেল, ভাবল দূর দূর, বিদেশ থেকে এসছো তো কি হয়েছে, যাও কথাই বলবোনা তোমার সাথে।ঘরে এসে দেখে ছোড়দা কী একটা কাগজ খুলে পড়ছে, ছেনু বলে এই শোন না, কানাডা কত দূরে রে?- অনেক দূর এখান থেকে, আমাদের হলো এশিয়া, তার পাশে ইউরোপ, তারপর আটলান্টিক মহাসাগর পেরিয়ে উত্তর আমেরিকার মধ্যে হলো গিয়ে কানাডা।- আমেরিকা মানে ওই দেশটা, যেটার ওপর তোর রাগ?- না উত্তর আমেরিকা একটা মহাদেশ, তার মধ্যে একটা দেশ আমেরিকা, তার পাশেই কানাডা।- যেখানেই হোক গে, একদম যাবি না কানাডায়, একদম যাবি না।ছোড়দা যারপরনাই অবাক হয়ে বলে, কেন কী হয়েছে কানাডায় গেলে? আর আমি খামোখা কানাডা যেতেই বা যাবো কেন?ছেনু ঠোঁট উল্টে বলে, ওখানে গেলেই তো সবাই বাংলা ভুলে যায়, বিচ্ছিরি দেশ!তবে ছেনু বেশিক্ষণ রাগ করে থাকতে পারলো না, একটু পরেই বদ্দি আর ছোদ্দির ডাক পড়ল পিসিমার ঘরে। ছেনুও পিছু পিছু গিয়ে দেখে, সেই সুবিশাল সুটকেসের একটা খোলা হয়েছে আর তার পেটের ভেতর কত্তো জিনিস। বদ্দি আর ছোদ্দির জন্য নকশাকাটা রঙিন কাঁচের শিশিতে করে কি একটা এনেছে। শিশির ওপরে একটু চাপ দিতে কি সুন্দর একটা গন্ধ বেরোলো। জিনিসটার নাম নাকি অডিকোলন, দুজনেই তো পেয়ে খুব খুশি (পরে একবার ওই শিশি কি ভেবে মা মাথাব্যথার ওষুধ হিসেবে মাথায় লাগাতে গিয়েছিল, মাঝে মধ্যে টুকটাক রাগ করলেও, বদ্দিকে ওইদিনের মতো অমন রেগে যেতে ছেনু কক্ষনো দেখেনি)। ছেনু সব বাইরে থেকেই দেখছিল। যদিও অন্য সময় পিসিমাদের ঘরে ছেনুর অবাধ যাতায়াত থাকে, তবে এখন তো ওকে ডাকেনি, কাছে যাবে কেন! মানসম্মান বলেও তো একটা জিনিস আছে না কি, মহারাজ বলে কথা। তবে ও বুঝতে পারল ওর কপালেও একটা দারুণ বিদেশি উপহার নাচছে। কারণ এ বাড়িতে তাকেই সবাই সবচে ভালোবাসে, দিদিদেরকে যদি এত সুন্দর জিনিস দেয়, তবে ওকে না জানি কি দেবে, ভেবেই ওর পেটের মধ্যে বুড়বুড়ি কেটে উঠল।ওই তো সুটকেস থেকে কি সুন্দর একটা জামা বের করছে, তবে বেশ বড়ই হবে ওর গায়ে। ওঃ, ওটা এনেছে কান্টুদার ভাইয়ের জন্য। এরপর বেরোল আর একটা কাঁচের বোতল , ওটা পিসিমার জন্য, পিসিমা সুগন্ধি খুব ভালোবাসে কিনা। এরপর একে একে বার হতে থাকল ছাতা, কলম, ব্যাগ, আরও কত কি। এক একটা জিনিস এক এক জনের জন্য। তারপর বেরিয়ে এল একটা বড়ো রঙচঙে টিনের গোলমতো বাক্স। ওমা! বাক্সটা কি সুন্দর দেখতে। একটা বরফের পাহাড়ের সামনে চকোলেটের ছবি। তাহলে এটা নিশ্চই বিদেশি চকলেটের বাক্স। যাক, এটাই তাহলে ছেনুর জন্য এনেছে। সত্যি কান্টুদার পছন্দের তারিফ না করে ছেনু পারে না। ওকি! বাক্সটা পিসেমশাইকে দিয়ে দিল কেন? আচ্ছা রাখতে দিল বোধহয়, পরে ওকে ডেকে দিয়ে দেবে, থাক যখন ডাকবে তখন আসবো, এখন আর দাঁড়িয়ে কাজ নেই।দুপুরে যখন কান্টুদারা খেতে বসল, সেও যেন এক দর্শনীয় বিষয়। সবাই দূরে দাঁড়িয়ে গোল হয়ে দেখছে। বেগুন ভাজা, পটল ভাজা, আলু ভাজা এসব খুবই পছন্দ হয়েছে বাচ্চাদের। সবকিছুই 'ডেলিশিয়াস' বলে হাসি মুখে খাচ্ছে চামচ দিয়ে। কান্টুদা হাত দিয়েই খাচ্ছে আর এটা ওটা করে ওদের খেতে সাহায্য করছে। জুলিবৌদি কান্টুদাকে ফিসফিস করে কি একটা জিজ্ঞেস করল, সম্মতি পেয়ে মাথা নেড়ে নিজেও হাত দিয়েই খাওয়া শুরু করল। পটলের ডালনা শুধু শুধু খেতে যাচ্ছিল, ডালটাও, কান্টুদা ভাতে মেখে খাওয়া দেখিয়ে দিল। মুশকিল হলো মাছের কালিয়া নিয়ে। বড় বড় পেটির মাছই দেওয়া হয়েছে কিন্তু না বুঝে বোনলেস ভেবে কামড় বসাতেই বিপত্তি। ঘটনা বুঝতে পেরে পিসিমা জলদি এসে কাঁটা গুলো টেনে বের করে দিলে, সবাই তৃপ্তি করে খেতে পারল। নতুন স্বাদের খাবার পেয়ে সবাই খুব খুশি, জুলিবৌদিও হেসে বলল, রিয়েলি আমেজিং ফুড। তা আবার পিসিমাকে রিলে করা হতে পিসিমার মুখে অবশেষে একটু হাসির রেখা দেখা গেল।এরপর আবার পাঁঠার মাংস খেয়ে সবারই পেট দমসম। কান্টুদা ছাড়া কেউ আর চাটনি খেতেই পারলো না। খাবার নিয়ে পিটার আর ম্যাক্সের আনন্দ দেখে পিসিমা পিসেমশাইকে শুনিয়েই দিলেন, কি গো তবে যে বলছিলে বাঙালি খাবার ওরা নাকি খেতে পারবে না!খাওয়া দাওয়ার পর পিসেমশাই বললেন, দাঁড়া বালিশ টালিশ সব পেতে বিছানা করে দিই, তোরা একটু গড়িয়ে নে। কান্টুদা শুনেই বলে, আরে না না, আমি হোটেল বুক করেছি তো! আসলে ওরা এখানে এডজাস্ট করতে পারবে কিনা ভেবে আগে থেকেই হিন্দুস্তান ইন্টারন্যাশনালে রুম বুক করে রেখেছি। আর এইটুকু জায়গায় এতজন আঁটবেও না।অবশ্য পিসেমশাই এর মনের মেঘ আবার কেটে গেল পরদিন যেই ওরা আবার হই হই করে হাজির। আজ পিটার আর ম্যাক্স এর দাবি বাড়িটা তাদের ভালো করে ঘুরে দেখাতে হবে, এই বাড়িটা নাকি তাদের ভারি পছন্দ হয়েছে। তাদের কথায়, ভেরি নাইস হাউস, লাইক অ্যান ওল্ড ম্যানসন, ফিলস ভেরি চার্মিং। কান্টুদার ভাইই আজ গাইড, ওর পিছন পিছন পিটার আর ম্যাক্স লাফাতে লাফাতে চলেছে। কান্টুদার সুটকেস থেকে আজকে আবার একটা দারুণ জিনিস বেরিয়েছে - একটা ঝকঝকে ইয়াশিকা ক্যামেরা। ব্যাগের মধ্যে থেকে লেন্স বের করে তাতে এঁটে, ফিল্মের কৌটো থেকে ফিল্ম বের করে পরালো। সেই ক্যামেরা চোখে লাগিয়ে এদিক ওদিক খচ খচ করে ছবি তুলছে আর মাঝে মাঝে জুলিবৌদিকে সব স্থান মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করছে। সাথে ছোড়দাকে নিয়ে ছেনুও তাদের পিছু ধরেছে, আরে হাজার হোক নিজের রাজত্বে বেড়াতে আসা বিদেশি অতিথিদের প্রতি মহারাজেরও তো একটা দায়িত্ব আছে নাকি! ছাদে গিয়ে তো ওরা ভীষণ আনন্দিত। দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে, ওপর থেকে নিচের সবকিছু খুদে খুদে দেখাচ্ছে, দারুণ হাওয়াও দিচ্ছে। এমনকি তখন সেই ছাদের থেকে হাওড়া ব্রিজ পর্যন্ত দিব্যি দেখা যেত। ছাদেও কান্টুদা অনেক ছবি টবি তুলল। ছেনুর মনে হলো আহা, পিটার, ম্যাক্স আর জুলি বৌদির সাথে দাঁড় করিয়ে ওর ছবিও যদি একটা তুলত!তবে মহারাজ ছনেন্দ্রনাথ সবচেয়ে বেশি দুঃখ পেলেন যখন দেখলেন, তাঁর জন্যই উপহার হিসেবে নিয়ে আসা বিদেশি চকলেট বাক্স থেকে বের করে পিটার, ম্যাক্স আর পিসেমশাই দিব্যি আনন্দ করে খাচ্ছে। সোনালি রাংতা দেওয়া কি সুন্দর দেখতে গোল গোল চকলেটগুলো! সে দৃশ্য দেখে তিনি নিজেকে সান্তনা দিলেন, আসলে চকলেটগুলো শুধু তাঁর জন্য নয়, সবার খাওয়ার জন্যই আনা হয়েছে, ঠিকই তো, ভালো জিনিস সবাইকে দিয়ে থুয়েই খেতে হয়। পরে যখন পিসিমা ডেকে হাতে দেবে, তখনই খাওয়া যাবে না হয়।কান্টুদারা মোট দিনদশেকের মতো ছিল কোলকাতায়। তারই মধ্যে ঠিক হল, ওরা নাকি দার্জিলিং ঘুরতে যাবে। একবার এতদিন পর ভারতে আসা হয়েছে, কলকাতার বাইরেও দু একটা জায়গা একটু ঘুরে দেখে নেওয়াই ভালো। শুনে ছেনুর ভারি মনখারাপ হয়ে গেল, সবে দুজনার সঙ্গে বন্ধুত্ব হবে হবে করছিল, তার মধ্যেই আবার ঘুরতে চলে যাবে। পাঁচ দিনের মধ্যেই অবশ্য ওরা আবার ঘুরেটুরে ফেরত আসতে বাড়িটা আবার হইচইয়ে ভরে উঠল। আর দুদিন পরেই কানাডায় ফিরে যাবে।কান্টুদাদের চলে যাওয়ার দিন তেতলার দাদা ছেনুকে ডাকতে এলো, যাবি নাকি প্লেন দেখতে? ছেনু তো শুনেই একলাফে রাজি। ছোড়দাকেও ডাকতে, ছোড়দা বললো আজ কলেজ আছে হবে না। যাই হোক, ছেনু মাকে বলে, একটা ভালো দেখে জামা পরে, পিসেমশাই আর দাদার সাথে রওনা দিল হিন্দুস্তান ইন্টারন্যাশনাল হোটেলে, দার্জিলিং থেকে ফিরে কান্টুদারা আবার ওখানেই উঠেছে, রাত্রে হোটেলে থাকত, আবার সকাল সকাল চান টান করে শেয়ালদায় চলে আসতো। হোটেলের লবি দিয়ে চারিদিকে তাকাতে তাকাতে ছেনু লিফটে চড়ে ওদের ঘরের দিকে গেল। ঘরে ঢুকে দেখে ওরাও বেরোনোর জন্য তৈরি। সুটকেস টুটকেস হাতে নেওয়ার পর জুলিবৌদি পিটার আর ম্যাক্সের দিকে একবার তাকাতেই তারা তড়াক করে উঠে খাটের তলা, বাথরুম, আলমারি, টেবিলের ড্রয়ার কোথাও কিছু জিনিসপত্র পড়ে আছে কিনা সব খুঁজে দেখে ফেলল। ছেনু তো কাণ্ড দেখে তাজ্জব।যাই হোক হোটেল থেকে দুটো ট্যাক্সিতে চেপে ওরা সবাই দমদম এয়ারপোর্টে পৌঁছে গেল ঠিক সময়ে। ব্যাগপত্র চেকিং টেকিংয়ের পর এবার বিদায়ের পালা। ক'দিনেরই বা দেখা, তবুও ছেনুর গলায় যেন একটা মনখারাপ দানা বাঁধছিল। ওরা একসময় শেষবারের মতো হাতটাত নেড়ে ঘেরাটোপের মধ্যে হারিয়ে গেল। পিটার আর ম্যাক্সও অনেকক্ষণ ধরে হাত নাড়ছিল ওদের দিকে ফিরে ফিরে, মানে যতক্ষণ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল আর কি। ওরা চলে যেতে দুঃখ কাটাতে পিসেমশাই দুজনকে নিয়ে গেলেন প্লেনের নামা ওঠা দেখাতে। তখন টিকিট কেটে একটা ঘেরা বারান্দা মতো জায়গায় দাঁড়িয়ে প্লেন দেখা যেত। ছেনু তো সার দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা প্লেনগুলো দেখে পুরো হাঁ। অবাক হয়ে দেখছে কত বড় বড় সব ডানাওলা বাস। জানলাগুলো সব এই পুঁচকে পুঁচকে লাগছে। ছেনু ভাবে এগুলো সব আকাশে ওড়ে কী করে? এতে চেপেই তো কান্টুদারা এসেছে! ওমনি দাদা আঙুল দিয়ে দেখাল দূউউরে একটা প্লেন মাঠের মধ্যে দৌড় লাগিয়েছে। যত এগোচ্ছে দৌড়ের বেগ বাড়ছে। এক সময় সামনের চাকাটা টুপ করে মাটি ছেড়ে আকাশে উঠে পড়ল।বাড়ি ফিরেও ছেনু ওদের কথাই ভাবছিল। এক সময় আর থাকতে না পেরে তেতলায় পিসিমার ঘরের দিকেই পা বাড়াল। গিয়ে দেখে পিসিমা কি সব সেলাই টেলাই করছে, সব ছুঁচ সুতো বের করেছে। পিসিমা ওকে দেখেই হেসে বললো কেমন প্লেন দেখলে বলো? ছেনু মাথা নাড়তেই পিসিমা বললো ওখানে একটা বাক্স রাখা আছে, আনো তো দেখি একবার। ছেনু তাকিয়ে দেখে সেই বিদেশি চকলেটের বাক্স। দৌড়ে গিয়ে তাক থেকে সেটা পিসিমার কাছে নিয়ে আসতে আসতেই ওর মনে একটা খটকা লাগল, এত হালকা কেন? তবে কি মাত্র অল্প ক'টা পড়ে আছে আর!পিসিমা বললো এনেছ, দাও তো। পিসিমা বাক্সটা খুলতেই ছেনু দেখে চকলেটের কোথায় কি, বাক্স বেবাক ফাঁকা! পিসিমা ছেনুকে বললো খেয়েছিলে তো চকলেট? কেমন লাগল? ছেনু বলে, কই না তো!- সে কি পিসেমশাই দেয়নি? আসলে চকলেট ভালোবাসে বলে বাবার জন্য এই চকলেটের বাক্সটা এনেছিল কান্টু। পিসেমশাই শুরুর থেকেই এমন টপাটপ খাচ্ছে, আমি বললাম দিও কিন্তু সবাইকে। তারপর খোকনও ওর বন্ধুদের কয়েকটা দিয়েছে। তারপর যে ক'টা পড়েছিল ওরা দার্জিলিং যাওয়ার সময় আমি সঙ্গে করে পাঠিয়ে দিলাম। ইসসস্ মাঝখানে যে তুমি বাকি পড়ে গেছ, এই দৌড়াদৌড়ির মধ্যে আমি খেয়ালও করিনি। তারপর বাক্সটা ধুয়েমুছে সরিয়ে রেখেছিলাম ছুঁচসুতো রাখব বলে।ততক্ষণে মহারাজ ছনেন্দ্রনাথ আর ওখানে থাকলে তবে তো! তিনি চোখের জল মুছতে মুছতে দোতলায় দৌড় মেরেছেন।পুনশ্চ: দুদিন পর আবিষ্কার হলো, কান্টুদা সেই দারুণ ইয়াশিকা ক্যামেরাখানা ভুলে এই বাড়িতেই ফেলে চলে গেছে। দার্জিলিং থেকে ফিরে রিল বদলাবে বলে বোধহয় সরিয়ে রেখেছিল, আর বের করা হয়নি। বাড়িতে ফটোগ্রাফি একমাত্র ছেনুর বড়দাই ভালো জানতো। তাই পিসেমশাই আর কি করবেন ভেবে না পেয়ে, সেই ক্যামেরা বড়দাকেই দিয়ে দিলেন। বড়দার হাত বেয়ে কালক্রমে সেই ক্যামেরাখানা বহুদিন পর মহারাজ ছনেন্দ্রনাথের হস্তগত হয় ও তা দিয়েই পরবর্তীকালে তিনি দেদার ছবিছাবা তোলেন। মহারাজের সিন্দুকেরই কোনো এক কোণে সেই প্রাচীন ক্যামেরা, লেন্স টেন্স সমেত আজও বহাল তবিয়তে বিদ্যমান। তা বিদেশি চকলেটের বদলে বিদেশি ক্যামেরা - এই বা মন্দ কি!বিপ্লবের আগুন - পর্ব নয় - কিশোর ঘোষাল | ছবি: রমিত চট্টোপাধ্যায়৯ওরা চলে যেতে ভল্লা গ্রামের দক্ষিণ দিকে হাঁটতে শুরু করল। গ্রামের এদিকটা এখনও তার দেখা হয়নি। এদিকে বসত কম। বিচ্ছিন্ন কিছু আবাদি জমি, আর অধিকাংশই অনাবাদি পোড়ো জমি। ভল্লা হাঁটতে লাগল। অনেকক্ষণ চলার পর তার মনে হল, সে গ্রামের সীমা ছাড়িয়ে এসেছে। জনহীন প্রান্তর - কিছু বড় গাছপালা, ছোটছোট ঝোপঝাড় সর্বত্র। আরও কিছুটা গিয়ে তার কানে এল বহতা জলের শব্দ। অবাক হল – এমন রুক্ষ প্রান্তরে কোথা থেকে আসছে এই ক্ষীণ জলধ্বনি। এগোতে এগোতে ভল্লা ছোট্ট একটা নালার পাশে দাঁড়াল। পূব থেকে পশ্চিমে বয়ে চলেছে জলধারা। খুবই সামান্য – কিন্তু ভল্লার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কোথা থেকে আসছে, এই জলধারা? এ অঞ্চলে বর্ষা হয় সামান্যই – তাহলে কোন উৎসমুখ এই জলধারাকে সজীব রেখেছে এই মধ্য শীতেও। এই গ্রামের অবস্থান চিত্রটি সে মনে মনে চিন্তা করল কিছুক্ষণ। এই গ্রামে আসার সময় পাহাড়ের কোলে রাজপথের ধারে সেই সরোবর দেখেছিল। সেই রাজপথ থেকে অনেকটাই নিচে এই গ্রামের অবস্থান। আজ সকালে যে দীঘির ঘাটে সে বসেছিল, সেটি এই গ্রামের পূর্ব সীমানায় এবং তার পরেই রয়েছে খাড়া অনুচ্চ যে পাহাড়টি – তারই শীর্ষে রয়েছে রাজপথের সরোবরটি। আজ সকালে গ্রাম পরিক্রমণের সময় আরও কয়েকটি পুকুর সে লক্ষ্য করেছে। তাহলে ওই দুই সরোবর, ওই পুকুরগুলি এবং এই নালার উৎস কি একই? প্রকৃতির কি আশ্চর্য লীলা – সরোবর কিংবা পুকুরগুলি কখনো প্লাবিত হয় না, কিংবা জলহীনও হয় না। ওগুলিকে সম্বৎসর পরিপূর্ণ রেখে উদ্বৃত্ত জলরাশি প্রবাহিত হয় এই নালাপথে! বর্ষায় হয়তো এই নালার প্রবাহ গতি পায়। ভল্লা আশ্চর্য হল। সে নালাপথের উজান বরাবর এগিয়ে চলল পূর্বদিকে। লক্ষ্য করতে করতে চলল নালার এপাশের জমির প্রকৃতি, গাছপালা ঝোপঝাড়। ভল্লার কৃষিকাজে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই। তবু রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে যেটুকু সে দেখেছে, তার মনে হল, আপাত অনুর্বর এই জমিকেও কৃষিযোগ্য করে তোলা সম্ভব। একটু পরিশ্রম করলে, এই নালার জল কৃষিকাজে সম্বৎসর ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রায় ক্রোশার্ধ হেঁটে সে পৌঁছল গ্রামের পূর্বসীমানার সেই পাহাড়তলিতে। এই জায়গাতেই পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসা একটি শীর্ণ জলধারা সমতলে নেমেছে। এই জায়গায় জলধারা কিছুটা বিস্তৃত, বড়ো বড়ো কিছু পাথর আর নুড়ির মধ্যে দিয়ে পথ করে কিছুদূর বয়ে গেছে। তারপরেই শুরু হয়েছে শীর্ণ নালা প্রবাহ। ভল্লা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করল, আশপাশের জমি-জায়গা। তার মনে হল, এই সব পাথর-নুড়ি আর মাটি দিয়ে গড়ে তোলা সম্ভব দুর্বল বাঁধ। তার উজানে বানিয়ে তোলা যেতে পারে ক্ষুদ্র জলাধার। এই স্থানটির অবস্থান যেহেতু একটু উঁচুতে, অতএব ওই জলাধার থেকে কৃত্রিম নালি কেটে জলকে চারিয়ে দেওয়া যেতে পারে সংলগ্ন নাবাল জমিগুলিতে। নিষিক্ত জমিতে চাষ করা যেতে পারে কিছু কিছু উপযোগী ফসল। ভল্লা দক্ষ সৈনিক, তীক্ষ্ণবুদ্ধি গুপ্তচর। দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় সে জানে, একটি গ্রামের সকল অধিবাসীকে কখনও উত্তেজিত করা যায় না। কতিপয় মানুষ বিদ্রোহী হয়। ভল্লা জানে এই গ্রামেরও নির্বিবাদী অধিকাংশ মানুষ হয় উদাসীন থাকবে, নয়তো ক্ষুব্ধ হতে থাকবে ভল্লার ওপর। বিদ্রোহী ছেলেদের বাবা-মা, দাদু-ঠাকুমা পরিজন সকলেই ভল্লার ওপর ক্রুদ্ধ হতে থাকবে, তাদের ছেলেদের “মাথাগুলি চিবিয়ে খাওয়ার” জন্যে। সেই ক্রোধ কিছুটা প্রশমিত হতে পারে, গ্রামের অর্থনৈতিক কিছু উন্নতির দিশা দেখাতে পারলে। সামান্য হলেও, ওই জলাধার এবং উদ্বৃত্ত কিছু ফসলযোগ্য জমির সৃজন, বাড়িয়ে তুলবে ভল্লার বিশ্বাসযোগ্যতা এবং গ্রহণযোগ্যতা। সন্ধ্যার কিছু আগে ভল্লা আগের জায়গাতেই ফিরে এল। সূর্য অস্ত গেলেও পশ্চিমদিগন্তে তার আলোর রেশ এখনও রয়েছে। বড়ো গাছের নিচে বসতে গিয়ে দেখল, তিনজন ছোকরা মাটিতে শুয়ে আছে। হাপরের মতো ওঠানামা করছে তাদের বুকগুলো। ভল্লা খুশি হল, কিন্তু চেঁচিয়ে ধমক দিল তিনজনকেই। বলল, “দৌড়ে এসে হাঁফাচ্ছিস, কিন্তু শুয়ে শুয়ে হাঁফাচ্ছিস কেন? একজায়গায় দাঁড়িয়ে কিংবা বসে হাঁফানো যায় না? ওঠ, উঠে বস। এতক্ষণের পরিশ্রমে পুরো জল ঢেলে দিলি, হতভাগারা”। ভল্লার কথায় তিনজনেই উঠে বসল এবং হাঁফাতে লাগল। ভল্লা বলল, “ধর শত্রুপক্ষের তাড়া খেয়ে, এ অব্দি নিরাপদেই এসেছিস। কিন্তু এরপর কী করবি?”“ওফ্। আগে একটু শ্বাস নিতে দাও ভল্লাদাদা”।ভল্লা আবারও ধমকে উঠল, “না, শ্বাস নিতে হবে, তার সঙ্গে ভাবনা চিন্তাও করতে হবে”। এই সময় আরও পাঁচজন ছেলে পৌঁছল। ভল্লা বলল, “বাঃ, প্রথম দিনেরপক্ষে ভালই – চল আমরা এসসঙ্গে নামতা বলি...এক এক্কে এক, এক দুগুণে দুই...জোরে জোরে চেঁচিয়ে...সবাই একসঙ্গে”। সন্ধের আগেই বাইশ জন এসে পৌঁছল, আরেকটু পরে পৌঁছল আরও বারো জন। সকলে একটু ধাতস্থ হতে ভল্লা বলল, “বিয়াল্লিশ জন ফিরেছিস দেখছি, বাকিরা?”“ওরা সরোবর অব্দি গিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে নামেনি, ফিরে আসছে গ্রামের পথেই”। ভল্লা হাসল, “এরকম রোজ দুবেলা দৌড়তে পারবি? খুব ভোরে আর আজকের মতো বিকেলে?” “পারবো”। “ঘোড়ার ডিম পারবি। কাল সকালে গায়ের ব্যথায় উঠতেই পারবি না। বোনকে দিয়ে গা-হাত-পা টেপাবি”।“পারবো”। কেউ কেউ বলল, কিন্তু তাদের গলায় আগেকার সে জোর নেই। ভল্লা হাসল, “কাল সকালে পায়ে, গায়ে, কাঁধে ব্যথা হবে। হবেই। কিন্তু কালকেও দৌড়তেই হবে, আজকের মতো এত তাড়াতাড়ি না হলেও – হাল্কা ছন্দে। একটু দৌড়লেই দেখবি – গায়ের ব্যথা কমে যাবে – কষ্ট কমে যাবে। আর দৌড়তে দৌড়তেও ভাববি, চিন্তা করবি – যা খুশি, যা তোর মন চায়। মনে রাখিস দৌড়লে আমাদের সর্বাঙ্গের পেশীর শক্তি বাড়ে। শক্তি বাড়ে আমাদের ফুসফুসের, আমাদের হৃদয়ের। কিন্তু মস্তিষ্ক? তার কী হবে? ভয়ংকর পরিশ্রমের মধ্যে, প্রচণ্ড আতঙ্কে, ভীষণ ক্লান্তিতেও আমাদের মাথা যেন কখনো অলস না থাকে। কোন কিছু না পেলে আমাকেই খুব গালাগাল দিবি। ভাববি কি কুক্ষণেই না ভল্লাদাদার কাছে গিয়েছিলাম। শয়তান লোকটা আমাদের সবাইকে খাটিয়ে মারছে, আর নিজে বসে বসে শুধু উপদেশ দিয়ে যাচ্ছে। ও হ্যাঁ, কাল সকালে আমিও তোদের সঙ্গে দৌড়বো। কমলিমায়ের যত্নে শরীরটা বড়ো অলস হয়ে উঠেছে – সেটাকে আবার চাঙ্গা করতে হবে”। অন্যদিনের তুলনায় আজ বাড়ি ফিরতে একটু দেরিই হল জুজাকের। কমলি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন – বারবার বেরিয়ে বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে গলা বাড়িয়ে পথের দিকে তাকিয়ে দেখছিলেন, মানুষটা আসছে কিনা। আজ অমাবস্যা। দুপাশের গাছপালা, ঝোপঝাড়ে গভীর অন্ধকার। তারার আলোয় পথটাকেই অস্পষ্ট ঠাহর করা যায়। পথের প্রেক্ষাপটে মানুষের অবয়ব বুঝতে পারা যায়। কমলির উদ্বেগ বাড়ছিল, জুজাক গ্রামপ্রধান ঠিকই, তবে তিনি শুনেছেন রাজধানী থেকে আসা রাজকর্মচারীরা অনেক ক্ষেত্রেই গ্রামপ্রধানকে সমীহ করে না। তারওপর জুজাক কিছুটা মুখফোঁড় বদরাগীও বটে। আধিকারিকদের কোনো তির্যক প্রশ্নের ব্যাঁকা উত্তর দিয়ে, পরিস্থিতি উত্তপ্ত করে তুলতে তার জুড়ি নেই। তার এই স্পষ্টবাদী সরল চরিত্রের জন্যেই গ্রামের মানুষ তাকে শ্রদ্ধা করে গ্রামপ্রধান বানিয়েছে। জুজাকের জন্য একদিকে কমলি যেমন গর্ব অনুভব করেন, অন্যদিকে ততটাই শঙ্কিতও থাকেন সর্বদা। তিনি জানেন দিনকাল বদলে চলেছে নিরন্তর। অপ্রিয় সত্যকথা কেউই সহ্য করতে পারে না। প্রশাসনিক আধিকারিকরা তো নয়ই। আজ অন্য আরেকটি বিষয়ও কমলির দুশ্চিন্তাকে বাড়িয়ে তুলেছে। ভল্লা। আজ গ্রামে সকলের সামনে সে নিজের মুখেই স্বীকার করেছে তার অপরাধের কথা। তার নির্বাসন দণ্ডের কথা। রাজকর্মচারীদের কাছে কী সে সংবাদ পৌঁছে গিয়েছে? যদি তারা জেনে গিয়ে থাকে ভল্লা জুজাকের ঘরেই আশ্রয় পেয়েছে। এই ঘরেই সে চিকিৎসা এবং সেবা পেয়ে সুস্থ হয়ে উঠেছে। সেটা কি তারা রাজদ্রোহীতা বলে মনে করবে? জুজাককে শাস্তি দেবে? কশাঘাত করবে? কিংবা বন্দী করে রক্ষীদের দিয়ে শারীরিক অত্যাচার করবে?হতভাগা ছেলেটা গেলই বা কোথায় কে জানে? নিজের ঘরে কিছুক্ষণ শুয়ে থেকে “আমি একটু ঘুরে আসছি, মা” বলে বেরিয়েছিল শেষ দুপুরে। এখনও পর্যন্ত তারও দেখা নেই। ঘরে থাকলে, একটু এগিয়ে গিয়ে দেখে আসতে পারত ছেলেটা। জুজাকের সঙ্গে যারা গিয়েছিল তাদের বাড়ি গিয়েও খবর আনতে পারত। বলা যায় না, জুজাক হয়তো, তাদের কারো বাড়িতে বসে জমিয়ে গল্প করছে। লোকটার কাণ্ডজ্ঞান ওরকমই। তার জন্যে ঘরে যে কেউ উৎকণ্ঠায় বসে আছে, সে কথা তার মনেই পড়ে না। ঘরবার করতে করতে কমলি লক্ষ্য করলেন, তুলসীমঞ্চের প্রদীপে তেল ফুরিয়ে এসেছে, সলতেটা ম্লান হয়ে জ্বলছে। দৌড়ে গিয়ে ঘর থেকে রেডির তেল এনে প্রদীপে ঢাললেন, সলতেটা একটু উস্কে দিলেন। আর তখনই বেড়ার দরজা খোলার শব্দ হল, চমকে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন, জুজাক ঢুকছেন। “এত রাত হল? কিছু গোলমাল হয়নি তো?”জুজাক কোন উত্তর দিলেন না, ঘোঁত করে নাকে শব্দ করে, দাওয়ায় বসলেন। কমলি দৌড়ে গিয়ে ঘটি করে পা ধোয়ার জল আনলেন। ঘর থেকে নিয়ে এলেন জুজাকের গামছাখানা। জুজাক ঘটির জলে পা ধোয়া শুরু করতে, কমলি বললেন, “কিছু বললে না, তো? এত দেরি হল কেন?”দুই পা ধুয়ে, গামছা দিয়ে ধীরেসুস্থে পা মুছতে মুছতে জুজাক বললেন, “গাঁয়ে ফিরেছি অনেকক্ষণ। ও পাড়ায় ঢুকতেই লোকজনের মুখে তোমার ছেলের গুণকীর্তন শুনছিলাম। তুমি শুনেছ?”“শুনেছি”।“তা আর শুনবে না? তোমার আদরের ছেলের জন্যে কাছারিবাড়িতেও আমাকে কত কথা শুনতে হল। খাবার জল দাও তো”। কমলি ঘর থেকে খাবার জল এনে দিলেন। “কী বলেছে তারা?”জুজাক মাটির ঘটি হাতে তুলে নিয়ে নিঃশেষ করলেন ঘটিটা। তারপর তৃপ্তির শ্বাস ছেড়ে বললেন, “হবে আর কী? গিয়েছিলাম কান্নাকাটি করে এ গ্রামের মানুষদের কিছুটা কর যদি কমানো যায়। অন্ততঃ সম্বৎসর সকলের পেটটা যাতে চলে যায়। সে কথায় কানই দিল না? বললে, ভল্লা তোমার বাড়িতে আছে? বললাম, আছে। বললে, একজন অপরাধী – যার রাজধানীর প্রশাসন থেকে নির্বাসন দণ্ড ঘোষণা হয়েছে। তাকে তুমি বহাল তবিয়তে খাওয়াচ্ছো, দাওয়াচ্ছো, চিকিৎসা করাচ্ছো। আর রাজার কর দিতেই তোমার নাকে কান্না শুরু হয়ে গেল?”কমলি উদ্বেগের স্বরে বললেন, “কী অবস্থায় ছেলেটা এসেছিল তুমি বললে না?”জুজাক একটু ঝেঁজে উঠে বললেন, “বলব না কেন? সবই বলেছি”। তারপর একটু থেমে নরম স্বরে বললেন, “ওরা রাজ কর্মচারী। তাদের কাছে ভল্লার পরিচয় অপরাধী। সে আর মানুষ নয়, জন্তু। ওদের কথা, ঘেয়ো কুকুরের মত যেভাবে এসেছিল, সেভাবেই ওকে তাড়িয়ে দিইনি কেন? জগৎটা তোমার মতো মায়ের মন নিয়ে যে চলে না, কমলি”।কমলি জুজাকের সহানুভূতির সুরে আশ্বস্ত হলেন। মানুষটাকে ওপরে ওপরে কঠোর মনে হলেও, মনটা নরম। তা যদি না হত, জুজাক জোর করেই ভল্লাকে তাড়িয়ে দিতে পারতেন। তৎক্ষণাৎ না হলেও, যেদিন ভল্লার প্রথম জ্ঞান হল, সেদিনই। আজকে রাজ-প্রতিনিধির যে তিরষ্কার তিনি শুনে এলেন – এমন যে হবে সেকথা জুজাক বহুবার বলেছেন। বারবার বলেওছেন, হতভাগাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেব – কিন্তু দিতে পারেননি। মানবিক বোধের কাছে তার বাস্তব যুক্তি হার মেনেছে। কমলি জিজ্ঞাসা করলেন, “কিন্তু ওদের কাছে এ খবর পৌঁছে দিল কে? নিশ্চই এই গাঁয়েরই কেউ?”“সে তো বটেই। সব গ্রামেই ওদের গুপ্তচর থাকে। তাদের কাজই তো ওদের খবর দেওয়া। সে যাক, ছোঁড়াটাকে ডাক দেখি একবার”।“সে তো সেই দুপুরের দিকে বেরিয়ে গেছে, এখনও ফেরেনি”।“কোথায় গিয়েছে তোমাকে বলেও যায়নি? আশ্চর্য। কবিরাজদাদার বাড়িতে আমরা বেশ কয়েকজন কথাবার্তা বলছিলাম। সেখানে শুনলাম, সকালে ভল্লার বক্তৃতা শুনে কয়েকজন ছোকরা নাকি বেশ বিগড়ে গেছে। দুপুরের পর থেকেই তারাও বাড়িতে নেই। তবে কি...”।কমলি আতঙ্কিত হয়ে বললেন, “তবে কি গো? ওই ছোঁড়াগুলো কি ভল্লাকে মারধোর করবে?”জুজাক হেসে ফেললেন কমলির সরলতায়, বললেন, “মেয়েদের লাঞ্ছনা রোধ করতে গিয়ে সে অপরাধী হয়েছে। রাজ-প্রশাসন লম্পট মানুষটাকে শাস্তি না দিয়ে, সাজা দিয়েছে ভল্লাকে। এ গাঁয়ের ছোকরাদের চোখে ভল্লা এখন বীর-নায়ক। কবিরাজদাদা বলছিলেন, ভল্লা বোধ হয় ছোকরাদের নিয়ে একটা দল গড়তে চাইছে”।কমলি অবাক হয়ে বললেন, “কিসের দল?”জুজাক আবার একটু ঝেঁজে উঠলেন, বললেন, “তার আমি কী জানি? তোমার মনে আছে, কবিরাজদাদা ওর শরীরের লক্ষণ দেখে বলেছিলেন, ভল্লা সাধারণ এলেবেলে ছেলে নয়। যথেষ্ট শক্তিশালী যোদ্ধা। আরও বলেছিলেন, ওই চরম অসুস্থ অবস্থায় ওর এখানে আসাটা হয়তো আকস্মিক নয়। হয়তো গোপন কোন উদ্দেশ্য আছে। আজকে সকলের সামনে কবিরাজদাদা সে প্রসঙ্গ তোলেননি। কিন্তু আমারও এখন মনে হচ্ছে কবিরাজদাদার কথাই ঠিক”।কমলি কিছু বললেন না। হাঁটুতে থুতনি রেখে গভীর চিন্তা করতে লাগলেন, ভল্লাকে দেখে কই আমার তো তেমন কিছু মনে হয়নি। এ গ্রামে আসা থেকে আমি তাকে যত কাছে থেকে দেখেছি, আর কে দেখেছে? তার কথাবার্তায়, তার মা ডাকে কোথাও কোন উদ্দেশ্যর সন্ধান তো তিনি পাননি। আজকে গ্রামের সবার সামনে মন খুলে নিজের অপরাধের কথা যে ভাবে সে স্বীকার করেছে, তার মনে যদি সত্যিই কোন পাপ বা অপরাধ বোধ থাকত, পারত ওভাবে বলতে?জুজাক বললেন, “খাবার বাড়ো, খেয়ে শুয়ে পড়ি”।কমলি তাড়াতাড়ি উঠে খাবার আনতে ঘরে ঢুকলেন। সেদিকে তাকিয়ে জুজাক বললেন, “তোমার ছেলে যত রাতই হোক বাড়িতে তো ঢুকবেই। তুমি ছাড়া তার জন্যে কে আর রাত জেগে খাবার কোলে বসে থাকবে? এলে বলে দিও, সামনের অষ্টমীতে ওকে সঙ্গে নিয়ে আমাকে কাছারি শিবিরে যেতে হবে। বলে দিও, না গেলে ওর তো বিপদ হবেই, আমাদেরও রক্ষা থাকবে না”।ক্রমশ...
হরিদাস পালেরা...
কি কিনি, কেন কিনি - সুকান্ত ঘোষ | ছোটবেলায় একটা কথা আমরা প্রায়ই শুনতাম, নানা প্রসঙ্গে – “সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র”। এখন আর ততটা শুনি না। কেন শুনি না তার নানা কারণ হতে পারে – আমাদের সত্যিই অগ্রগতি হচ্ছে সমাজ হিসেবে যেখানে শুধু সৌন্দর্য্য দিয়ে আমরা কারো যোগ্যতা বিচার করছি না; বা আমি সমাজের একাংশ যেখানে ‘মনে যাহা আসে বলে ফেল’ থেকে সরে এসে সমাজের একাংশের সাথে সময় কাটাচ্ছি যেখানে ‘পটিলিক্যালি কারেক্ট’ কথাবার্তা বলা একটা আবশ্যিক অঙ্গ বলে বিবেচিত হয়; বা ‘ডাইভারসিটি অ্যান্ড ইনক্লুশন’ ব্যাপারটিতে আমরা অনেকেই সচেতন হয়ে পড়ছি, সে কেউ ব্যক্তিগত ভাবে ব্যাপারটাকে তত গুরুত্বপূর্ণ মনে করুক বা না করুক। তাহলে তো মনে হতেই পারে এবার যে – যাক আমরা তাহলে যুগের সাথে বাহ্যিক সৌন্দর্য্যের উপর আমাদের যে পক্ষপাত তার থেকে বেরোতে পেরেছি। মানুষকে তার যোগ্যতা দিয়েই কেবল বিচার করছি। হ্যাঁ, এটা হয়ত ঠিক যে যখন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বৃহত্তর জনগণের স্বার্থে, সেখানে আমরা অনেক সচেতন হয়ে পড়েছি – কিন্তু একই কথা কি বলতে পারি যখন সেই আমরাই কেবলমাত্র ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত নিই ব্যক্তিগত কাজের জন্য?মোটামুটি ভাবে এর উত্তর হল – না। সুন্দর জিনিসের প্রতি পক্ষপাতের উর্দ্ধে আমরা পুরোপুরি উঠতে পারি নি। সচেতন হয়েছি ঠিক, কিন্তু আমাদের মস্তিষ্ক, আমাদের অভিযোজন – আমাদের অবচেতনে সুন্দরের প্রতি পক্ষপাতের বীজ খুব গভীর ভাবে পোঁতা হয়ে আছে। অনেকেই বুক বাজিয়ে বলবেন, আমি এই সবের উর্দ্ধে। কিন্তু প্রচুর সংখ্যক বৈজ্ঞানিক গবেষণা আছে যে প্রমাণ করেছে, আমরা প্রায় কেউই সেই পক্ষপাতের উর্দ্ধে নই। আসলে আমরা অনেক সময় টেরই পাই না যে কি ভাবে আমাদের মস্তিষ্ক কিছু সিদ্ধান্ত নিতে আমাদের চালিত করেছে।মানুষের সুন্দরের প্রতি এই পক্ষপাতের দিকটা বলাই বাহুল্য অনেকে নানা ভাবে ব্যবহার করেছে – সবচেয়ে বেশী মনে হয় হয় ব্যবহার করেছে বিজ্ঞাপনদাতারা এবং কনজিউমার মার্কেট। এদের থেকে বেশী কেউ আমাদের ম্যানুপুলেট করে নি – কারণ বাকি সবার থেকে এরা নিজেদের অভিজ্ঞতা দিয়ে জানে যে মানুষের সৌন্দর্য্য কিভাবে আমাদের সাথে কৌশলের খেলা খেলে – যুগ যুগ ধরে, বারেবারে। এরা জানে আমরা কিভাবে সুন্দর শিশুর মুখের দিকে একটু বেশীক্ষণ তাকিয়ে থাকি, পুরানো দিনে স্লাইডের ব্যবহারের থেকে কেউ পাওয়ার পয়েন্ট ব্যবহার করলে তাকে একটু বেশী এগিয়ে রেখেছি ইত্যাদি।আমরা ধরে নিই বা মনে করি আকর্ষণীয় মানুষেরা বেশী বুদ্ধিমান, বেশী সৎ, আবেগ নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে বেশী সামঞ্জস্যপূর্ণ – মানে সাধারণ জনতার সাথে এরা সব ব্যাপারেই এগিয়ে। যদি বাকি সব কিছু কাছাকাছি স্তরের হয়, তাহলে আমরা এখনও যে সুন্দর দেখতে তাকে বেছে নিই কিছু প্রেজেন্ট করার জন্য; এক ওভার বাকি আছে টেষ্ট ম্যাচ শেষ হতে, একটাই উইকেট - কে ব্যাট করবে আমার হয়ে; কে প্লেনে খাবার সার্ভ করবে আমাদের, এমনই পাইলটকেও। এবার ব্যাপার হল আমি উপরে যা লিখলাম তা আপনি বিশ্বাস নাও করতে পারেন। যদি বলি এগুলো শুধু আমার মত নয়, এই নিয়ে অনেক স্টাডি হয়েছে – এবং যা লিখলাম তা স্ট্যাটিসটিকস এর উপর ভিত্তি করে, তাহলেও আমাদের অনেকের কাছে উত্তর রেডি আছে, “দেয়ার আর লাইজ, ড্যাম লাইজ, অ্যান্ড স্ট্যাটিসটিকস”। মানে স্ট্যাটিসটিকস ব্যবহার করে যা কিছু চাও তাই প্রমাণ করা যায়।কিন্তু এটা সত্যি নয়। স্ট্যাটিসটিকস কোন ক্ষেত্রেই মিথ্যে বলে না যদি তা ঠিক মত ব্যবহার করা হয়। আর এই ক্ষেত্রে মিথ্যে তো নয়ই। কেন নয় সেই সব বিস্তারে এখানে লেখার সুযোগ নেই। শুধু বলি, যাঁরা ওই গবেষণাগুলির স্ট্যাটিসটিকস এ বিশ্বাস করেন নি, বা সৌন্দর্য্যের উপর আমাদের পক্ষপাতের ব্যাখায় – তাঁদের জিজ্ঞেস করা হয়েছিল – ঠিক আছে, এই ব্যখ্যা মানতে হবে না। তাহলে কিসের উপর ভিত্তি করে আপনি ওই বিশেষ ব্যক্রি বা বস্তু পছন্দ করেছিলেন?তার উত্তর এসেছিল – “ইট জাষ্ট ফেল্ট রাইট”এর পরে আসবে কোটি টাকার প্রশ্ন, সুন্দর সুন্দর বলে তো হইচই করছ। আমাদের কাছে আসলে সুন্দর তাহলে কি? তোমার কাছে যা সুন্দর, আমার কাছে তো তা সুন্দর নাও হতে পারে!এই নিয়েও গুচ্ছ গুচ্ছ গবেষণা বা লেখাপত্র আছে। অবশ্যই আমার কাছে যে সুন্দর তা আপনার কাছে নাও হতে পারে। কিন্তু একটা জেনেরিক ব্যাপার আছে, যা আমাদের মস্তিষ্কে প্রোথিত আছে আমাদের বেড়ে ওঠা, আমাদের অভিযোজন এদের সাথে। কেন সুন্দর না ব্যাখ্যা করতে না পারলেও, সুন্দর তা আমাদের মস্তিষ্ক মনে নেয়। যেমন, ঐশ্বর্য্য রাই সুন্দর এটার সাথে দ্বিমত হবে এমন খুব বেশী মানুষ পাবেন না – যদিও প্রায় আমরা অনেকেই ব্যাখ্যা করতে পারব না যে ওকে সুন্দর বলছি কেন!এগুলো আরো জটিল হয়ে ওঠে গভীরে গেলে – ছোটবেলা থেকে আমরা শিখে আসি যে সুন্দর জিনিস আমাদের জন্য ভালো। এই জন্যই দীর্ঘ সময় হিন্দী সিনেমার (বা অন্য সিনেমাতেও) ভিলেনরা বিশেষ একধরণের দেখতে বা বিশেষ এক ধরণের ব্যবহারের স্টিরিওটাইপ হত বা এখনও হয়। আমাদের মস্তিষ্কে প্রোথিত আছে যে ধারালো, ছুঁচালো, অমসৃণ, বিবর্ণ – এমন সব জিনিস সব বিপদজনক হতে পারে – আর অন্যদিকে মসৃণ জিনিস হল নিরাপদ। তাই মসৃণ ত্বকের মানুষের মুখের উপর আমাদের নজর এবং পক্ষপাত বেশী যায়, ব্রণ ভর্তি বা পক্সের কারণে দাগ থেকে যাওয়া মুখের থেকে। এই এখনও দেখা গ্যাছে যে কোন টিম কালো জার্সি/ড্রেস পরে খেললে, রেফারীরা বেশী সহানুভূতি তাদের উপর দেখায় না। কালো, ধূসর রঙের সাথে জুড়ে আছে এমন ট্যাবু। শুধু রঙ বা মসৃণতাই নয়, কোন জিনিসের আকারের উপরেরও আমাদের এমন অবচেতন পক্ষপাত আছে। কি মনে হয়, কোন আকারের (সেপ) উপরের আমাদের পক্ষপাত বেশী? এর উত্তর সোজা – আপনারাও জানেন, তবে সেটা দেবার আগে একটা ছোট্ট গল্প শোনানো যাক।১৯৬৩ সালের কথা – “স্টেট মিউচ্যুয়াল লাইফ ইনসিওরেন্স অব আমেরিকা” কোম্পানী তখন সবে অন্য একটা ইনসিওরেন্স কোম্পানীকে অধিগ্রহণ করেছে। স্বাভাবিক ভাবেই সেই অধিগ্রীহিত কোম্পানীর কর্মচারীদের মানসিক অবস্থা বা ‘মরাল’ তেমন যুতের নয়। তখন সেই বড় কোম্পানীর কর্তারা ভাবতে বসলেন যে কিছু করে কি এই নতুন কর্মচারীদের মরাল এর উন্নতি করা যায়? ডাকা হল তখনকার দিনের বিখ্যাত অ্যাডভার্টাইজ এবং পাবলিক রিলেশন বিশেষজ্ঞ হার্ভে বল-কে। হার্ভের তখন নিজের ফার্ম ছিল ম্যাসাচুয়েটস-এ। তিনি প্রথমে ওই ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর প্রস্তাব শুনে ভাবলেন, এ আবার কেমন কাজের অনুরোধ! কিন্তু তবুও বললেন, তিনি ভেবে দেখবেন। হার্ভে-কে খুব বেশী দিন এই নিয়ে ভাবতে হয় নি। ইনফ্যাক্ট যেদিন তিনি এই অ্যাসাইনমেন্টের প্রস্তাব পান, সেই দিনই বিকেলে তিনি ড্রয়িং বোর্ডের সামনে ভাবতে শুরু করে একসময় এঁকে ফেললেন একটা হলুদ বৃত্ত, এবং তার ভিতরে দুটো ছোট বৃত্ত এবং একটি অর্ধবৃত্ত!চিনতে পারছেন এটা? হ্যাঁ, এই সেই আজকের দিনের বিখ্যাত ‘স্মাইলি’ ফেস। এই কাজের জন্য হার্ভে একমাস পরে চেক পেয়েছিলেন তখনকার দিনে ৪৫ ডলার, যা আজকের দিনে হিসেব করলে প্রায় ৫০০ ডলারের মত। এর পরের কয়েক বছরে কি হতে চলেছে তা মনে হয় হার্ভে নিজেও আন্দাজ করতে পারেন নি – তাঁর দ্বারা সৃষ্ট সেই স্মাইলি ফেস আমেরিকার পোষ্টাল স্ট্যাম্পে স্থান পাবে, ওয়ালমার্টের সিম্বল হিসেবে দেখা যাবে, যা থেকে বানানো হবে ‘বাটন’ বা স্মাইলি চাকতি/বোতাম, কেবলমাত্র ১৯৭১ সালে পাঁচ কোটি বিক্রী হয়েছিল! এ এক প্রত্যক্ষ প্রমাণ কোন এক আকারের স্বাভাবিক সরলতা – যা থেকে আমরা একদম ছোটবেলা থেকেই আকৃষ্ট – বৃত্ত।তাহলে উত্তর পেয়ে গেলেন তো যে, কোন আকারের (সেপ) উপরের আমাদের পক্ষপাত বেশী? সেই আকার হল গোল বা বৃত্ত।বিখ্যাত ডিজাইনার-রা আমাদের বৃত্তের প্রতি এই পক্ষপাত-কে বিস্তারে ব্যবহার করবে না, তা তো হয় না! যে কোন জিনিসের মতন, নানা কোম্পানীর লোগো-কেও র্যাঙ্ক করা হয়েছে ক্রেতাদের পছন্দ অনুযায়ী – মানে পৃথিবীর সবচেয়ে জনপ্রিয় ২৫টি লোগো কি, এমন প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে দেখা গ্যাছে প্রত্যাশা অনু্যায়ী সেই লোগো গুলিতে ‘বৃত্ত’-র ব্যবহারের প্রাচুর্য্য। বি এম ডব্লু, মার্সিডিজ, নাসা, অ্যাপেল, স্টারবাক্স, পেপসি, লন্ডন আন্ডারগ্রাউন্ড, গুগুল, মাষ্টারকার্ড – ইত্যাদি সবজায়গাতেই বৃত্তের ব্যবহার। যাই হোক, এখানে শুধু কি আকার, রঙ ইত্যাদির উপর আমাদের আকর্ষণ বেশী সেই নিয়ে হালকা আলোচনা করলাম, কিন্তু কেন সেই আকর্ষণ সেই নিয়ে পরিপূর্ণ আরো বই এবং পেপার আছে। হ্যারি বেকউইথ লিখিত ‘আনথিঙ্কিং’ বইটির বিস্তার আরো বেশী। এই বইতে আলোচনা করা হয়েছে আমরা যখন কিছু কিনি, সেই কেনার পিছনে আমাদের অজান্তেই কি ফোর্স কাজ করে, আমাদের অবচেতন পক্ষপাত কিভাবে আমাদের সিদ্ধান্ত-কে প্রভাবিত করে – এবং সবথেকে বড় কথা আমাদের সেই দূর্বলতা ব্যবহার করে কিভাবে মার্কেটিং স্ট্রাটেজি তৈরী করা হয়। আমরা ভেবে নিচ্ছি এটা তো আমার একারই সিদ্ধান্ত, এর মধ্যে কারো প্রভাব নেই – আমরা জানিও না খুব সূক্ষ্ম ভাবে কিভাবে আমাদের সেই সিদ্ধান্ত নেবার কিনারে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল কেউ/কারা যাদের অস্তিত্ত্ব সম্পর্কে আমরা সর্বদা অবগতও থাকি না। অ্যাডভার্টাইজমেন্ট জগতে পাঁচটা প্রধান ব্যাপার – কনসিভ, ডিজাইনিং, পজিশনিং, নেমিং এবং প্যাকেজিং – এগুলো নিয়ে নিয়ত গবেষণা চলেছে। আপনি এবং আমি সেই গবেষণায় নিয়মিত তথ্যের যোগান দিচ্ছে। কিভাবে? ফেসবুক সহ যা কিছু ফ্রী ওয়েবসাইট এবং অ্যাপ ব্যবহার করে!হ্যারি বেকউইথ এর ‘আনথিঙ্কিং’ বইটি প্রায় তিনশো পাতার। একবার শুরু করলে শেষ করতেই হবে এমন ইন্টারেষ্টিং। বইয়ের নামঃ Unthinking – The Surprising Forces Behind What We Buyলেখকঃ Harry Beckwithপ্রকশকঃ Business Plus, New York, 2011বাবা এবং ঈদ - মোহাম্মদ কাজী মামুন | আজ সন্ধ্যায় আমার পচাত্তর ছুঁইছুঁই বাবা বললেন, ''আমি তোমাদের তিন ভাইবোনকে ঈদের জামা কিনে দিতে চাই। আগামী বছর আর ঈদ পাবো কিনা জানি না।'' আব্বা অবসরের পনের বছর পূর্ণ করার পর সরকার থেকে একটি মাসিক সন্মানি পেতে শুরু করেছেন। সেই টাকা থেকেই তিনি তার সন্তানদের ঈদ উপহার দেয়ার কথা ভাবছেন জীবন সায়াহ্নে দাঁড়িয়ে। আব্বার কথাটা শুনে হৃদয়ের গভীরে ভীষন মোচড় অনুভব করলাম .......... স্মৃতির সিড়ি দিয়ে নামতে নামতে চলে গেলাম সেই শৈশবের কোন এক ঈদে, আব্বা সংসার চালাতে হিমশিম খাচ্ছিলেন, মামারা ইতোমধ্যে ঈদের শার্ট, প্যান্ট কিনে দিয়েছেন, খালা কিনে দিয়েছেন জুতো, কিন্তু এরপরও আমি কাঁদো কাঁদো, আমার যে অন্য সবার মত দুই সেট জামা চাই, সকাল ও বিকালে বদলে পরার জন্য, আমার বাবার হাতে টাকা নেই, বোনাসের টাকা দোকানের ধার শোধেই ব্যয় হয়েছে, আমাদের ভাইবোনদের মুখের দিকে তাকিয়ে আর বসে থাকতে পারলেন না, আমার সেজ ফুপা থাকেন চট্রগ্রামে, তার কাছে থেকে কিছু টাকা নিয়ে এলেন ঈদের দুদিন আগে, মনে পড়ে, আমায় নিয়ে গিয়েছিলেন গুলিস্তানের একটি সদ্য নির্মিত মার্কেটে, দোকানে ঢুকেই ছোটদের জন্য টানানো একটি কমপ্লিট স্যুটের দিকে আঙ্গুল তাক করে ফেললাম, সেই হাত আর নামাতে পারলেন না তিনি, অবশেষে বাজেটকে তছনস করে সেই স্যুট বগলদাবা করে মহানন্দে বাসায় ফিরলাম। সংসারের ঘানি টানতে গিয়ে সার্ভিস বেনিফিট আব্বাকে আগেই তুলে ফেলতে হয়েছিল, তাই যখন অবসরে যান, তখন নিজের অবসর-উপার্জন বলতে তেমন কিছু ছিল না। আমরা ভাইবোনেরা সবাই মিলে বাবাকে ঈদের পাজামা-পাঞ্জাবি কিনে দিয়েছি সবসময়। ...আজ এত বছর পর নিজের উপার্জন হাতে পেয়ে আব্বা তার সন্তানদের আবার ঈদের জামা কিনে দিতে চাইছেন, আব্বা কি সেই সময়ে ফিরে যেতে চাইছেন? মিস করেন সেই সময়টুকু? নিজে উদোম থেকেও সন্তানকে ঈদের দিনে সুন্দর পোশাক পরানোর আনন্দটুকু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা? আমি বললাম, ' কোন দরকার নেই, আব্বা। উমরাহ হজ্বে যাওয়ার জন্য টাকাগুলো জমানো হচ্ছে, সেইভাবেই থাকুক।' বাবার উত্তর, '' চারদিকের যে অবস্থা, আগামী বছর পর্যন্ত নাও বেঁচে থাকতে পারি, বাবা ! উমরাহ হয়তো করা হবে না, আমার ইচ্ছা, তোমাদের ভাইবোনদের এই শেষ সময়ে কিছু একটা উপহার দেই।'' ...শৈশবে বাবার কাছ থেকে ঈদের পোশাক পেলে খুশীতে মন নেচে উঠতো, কিন্তু আজ বাবার কথাটা শোনার পর থেকেই ভিতর হতে গুমড়ে গুমড়ে উঠছে কান্না ...... চোখ ভিজে উঠছে বারবার কোন এক অজানা বেদনায়...... মানুষের জীবন এত বৈপরিত্যে ভরা কেন? কেন এত অদ্ভুত বিষাদমাখা?আমাদের বাবা - Eman Bhasha | আমার বাবা।। সারাজীবন ঠোঁট কাটা এবং গরিব আদিবাসী দলিতের বন্ধু ছিলেন। আড়ালে আবডালে বলা হতো-- সাঁওতাল বাগদি মুচি ছোটলোকদের নেতা। প্রকাশ্যেই বলতেন অনেকে: ছোটলোকদের মাথায় তুলছে। গরিব মানে ৭০ এবং আশির দশকের মাঝ পর্যন্ত ছিল 'ছোটলোক'। গরিবপাড়াকে মধ্যবিত্তরা বলতেন, 'ছোটলোকদের পাড়া'। বাবাদের সংগ্রাম ছিল একে বদলানো। তাই মুচিপাড়া হল দাসপাড়া। বাগ্দিপাড়া রসপুকুর। সাঁওতাল পাড়া প্রথমে আদিবাসী পাড়া পরে খাবড়িগড়।#সমানে তর্ক করেছি তাঁর সঙ্গে। ছোট থেকেই। তিনিই শিখিয়েছিলেন তর্ক। তিনিই বলেছিলেন, যুক্তি ছাড়া কিছু মানবে না। আমি বললেও না। আগাছা হয়ো না গাছ হয়ো। বঞ্চিতদের পাশে থেকো। নিন্দা প্রশংসার মুখাপেক্ষী হয়ো না।'#আর একটা কথাও বলতেন-- বন্ধু মহলে-- বিচারসভায়।চুলে কখনও ছেলে আটকায় না।চুলের হিন্দি প্রতিশব্দটি ব্যবহার করতেন, বলাই বাহুল্য।বলতেন, দোষহীন মানুষ হয় না। কম বা বেশি দোষ। তবে সৎ মানুষ হওয়া যায়। চুরি না করেও বাঁচা যায়। বন্ধু কৌশিক ভট্টাচার্য মনে করালেন কবিতার কথা। কবিতা লিখতেন। গান করতেন । সুর দিতেন।এক অনিন্দ্য ব্যানার্জি ছাড়া একসঙ্গে কারও এতগুণ আমি চেনাবৃত্তে দেখিনি।# আমার দেখা সেরা কমিউনিস্ট। জমি বেচে পার্টি করেছেন।১৯৫৭ তে পার্টির সংস্পর্শে আসেন। ১৯৮৭ তে পার্টি সদস্যপদ ছেড়ে দেন। চিঠি লিখে বলেন, আমি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হওয়ার যোগ্য নই, কারণ আমার কিছু জমি আছে। পরের পংক্তি ছিল: এই পার্টির কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ দেওয়ার যোগ্যতা নেই। কারণ এই পার্টিটা কমিউনিস্ট পার্টি আর নেই । বড়লোকের ধামাধরা হয়ে উঠছে।## সারা বছর পার্টিকে গাল দিতেন। ভোট এলেই জানপ্রাণ দিয়ে পার্টিকে বাঁচানোর জন্য খাটতেন।২০০৯ তে যখন পার্টির ব্রাঞ্চ সদস্যরাও তৃণমূলের কাছে মুচলেকা দিয়ে দিল, তিনি বলেছিলেন, কাউকে মুচলেকা দিতে শিখিনি। একঘরে করা হয়েছিল। দমেন নি।১৯৮৭ তে পার্টি ছাড়ার পর কারো কারো মদতে পুকুরে বিষ পালুইয়ে আগুন দেওয়া হয়েছিল। আর ২০০৯ থেকে একঘরে। মানুষ কথা বলতো লুকিয়ে২০১৩ যে পার্টি পঞ্চায়েত নির্বাচনে যখন ভয়ে প্রার্থী দেবো না ঠিক করল নিজে ক্যান্সার রোগী হয়ে গ্রামে গ্রামে বেরিয়ে পড়লেন ৭৯ বছর বয়সে প্রার্থী খুঁজতে। যেখানে পঞ্চাশ ষাট ও সত্তর দশকে পার্টি গড়েছিলেন। ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে হারা আসনে জেতালেন পার্টিকে। প্রচারক দুজন। আমার বাবা। আর পার্টি/ সমাজসেবা করে সম্পত্তি উড়িয়ে দেওয়ার জন্য দৈনিক গাল দেওয়া আমার মা। একাই লিখে বেড়ালেন দেওয়াল। একাই গেলেন গণনাকেন্দ্রে।মুসলিম ছাড়া কোনও দিন প্রার্থী করেনি যে আসনে কোন পার্টি সেখানে দাঁড় করালেন এক চর্মকারের সন্তানকে। জেতালেন।গোটা থানায় কোন লাল পতাকা উড়ত না। শুধু আমাদের বাড়িতে। ২০১৩ ভোটে জেতানোর পাঁচ মাস পর চলে গেলেন বাবা।মা সেই পতাকা রেখেই ছিলেন উড়িয়ে।কিন্তু মায়ের মৃত্যুর পর কোন নেতা এলেন না। যাঁরা সত্তর দশকে আশ্রয় নিয়েছিলেন। কষ্ট পেয়েছি। কিন্তু কমিউনিস্ট মতাদর্শ এবং গরিবের পাশে থাকা ভুলি নি।#বাবা নাটক যাত্রা থিয়েটার করতেন। সাঁওতালদের সঙ্গে নাচতেন। খেলতেন সব ধরনের খেলা।সত্যম্বর অপেরায় যাত্রা করতে উৎপল দত্তের সংস্পর্শে আসেন। গ্রামে কংগ্রেসীদের সঙ্গে নিয়েই একযোগে সবাই মিলে, জুনিয়র হাইস্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন।সহযোগী ছিলেন আমার বড় মামা। কংগ্রেসের দাপুটে শিক্ষক নেতা। কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল অটুট। মুখে যদিও বলতেন, বন্ধুর চেয়ে পার্টি বড়। কাজে ব্যক্তিগত সম্পর্কে বিশ্বাসী ছিলেন।আমার ভাইয়ের বিয়ের সময় বউয়ের নাম/ পদবী বদলাতে হবে বলায় আপত্তি করেন। আমাদের অত্যন্ত প্রিয় এক আত্মীয় বলেন, হিন্দু নাম থাকলে আমরা কেউ খাবো না। চলে যাবো-- বাবা উত্তর দেন, এটা তোর ব্যাপার। তাঁরা চলে গেলেন। বাবা একবারও অনুরোধ করলেন না।আমাদের খারাপ লাগছিল।কিন্তু বাবার হ্যাঁ তো হ্যাঁ না তো না।যুক্তি বুদ্ধি দিয়ে যা বুঝবেন তাই করবেন।নাড়ায় কার সাধ্য।আমি মানবধর্মে এবং নবীর কথায় বিশ্বাসী। আমার ধর্ম আমার কাছে তোমার ধর্ম তোমার কাছে।একবার একজন রাগের মাথায় তালাক দিয়ে দেন। দিয়ে খুব কষ্ট পান। তিনি খুব ধর্মবিশ্বাসী। তাঁর বাবা এবং স্ত্রীও ধর্মপ্রাণ।কী হবে? খুব শোরগোল।শহর আর গ্রাম বা বস্তি এক নয়।সবাই সবকিছুতে যোগ দেয়। হিন্দু মুসলমান মিলে লোকে লোকারণ্য।বাবা খবর পেয়ে এলেন। দুজনকে টেনে দোতলায় নিয়ে গিয়ে ঘরে ঢুকে দিনে দুপুরে শিকল তুলে দিয়ে বললেন, যা। মেটা ঝামেলা।সেকালে বিশ্বাস ছিল, স্বামী স্ত্রীর সব ঝামেলা বিছানায় মেটে।নারীবাদীরা রাগবেন না। তাঁরা এখন সুখী দম্পতি। তাঁদের নাতনির বিয়ে হল কদিন আগে।#আরেকজন বাবার খুব ভক্ত। দাবা খেলার পার্টনার। রেগে তালাক দিয়ে বসলেন। কী হবে এবার? খুব চিন্তা। বাবা বললেন, তুমি তো কমিউনিস্ট পার্টি করো। তোমার আবার তালাক ফালাক কী।আর ধর্মেও তিন তালাক নাই। আমি বাংলায় কোরান পড়েছি।যাঁরা পড়েনি তাদের কথা শুনো না। তারা না পড়ে বড্ড বেশি ফরফরায়।আর যাঁরা আমাকে তৃণমূলের দালাল বলে আনন্দ পান-- তাঁদের জন্য, আমার বাবার গায়ে লাল পতাকা জড়িয়ে দিয়েছিলাম ধর্মীয় নেতা আর তৃণমূলের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে। কেউ কেউ বলেছিলেন, বাবার সঙ্গে আমাকেও কবরে পুঁতে দেবে গাঁয়ে ২০০৯ এর পর লাল পতাকা বের করায়। ২০১৬ তে আক্রান্ত হয়েছি শাসকদলের অন্যায় কাজের বিরোধিতা করায় জন্মভূমিতে। ২০১৮ তে দুবার কর্মক্ষেত্রে। কাজ করে দেখাতে হয়। ফেসবুকে বাণী দিয়ে নয়।সংযোজন:#কাদামাটির_হাফলাইফ ৪৫আমার বাবার গল্প শুনতে চেয়েছেন এক মনস্ক পড়ুয়া বন্ধু। পৃথিবীর সব বাবার মতোই আমার বাবা স্বভাবে ভোলে ভালা। বাড়ির কথা মনে থাকে না, কিন্তু যখন থাকে তখন খুব মুশকিল। যা করবেন ১০০ শতাংশ। যা ছাড়বেন তাও একশো শতাংশ। খালি সামাজিক কাজ আর পড়া লেখার অভ্যাস ছাড়তে পারেন নি। মৃত্যুর দিন সকালেও বই পড়েছেন। হাসপাতালে শুয়ে শুয়ে গুনগুন করে গান গেয়েছেন। আলিপুর কমান্ড হাসপাতালের শয্যায় শুয়ে এপিটাফ লিখেছেন।বাবা পার্টির কাজে কয়েকদিন কিন্তু যাত্রা নাটকের কাজে মাসের পর মাস উধাও হয়ে যেতেন। পেশাদারি যাত্রাদলেও একাধিকবার কাজ করেছেন। খ্যাতনামা সত্যম্বর থেকে বর্ধমান বাঁকুড়া মেদিনীপুরের দল শ্রীদুর্গা অপেরা বা আরো কোন দলে।রাখাল সিংহ, চণ্ডী কেস ছিল তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধু। যাত্রাপালাকার শম্ভু বাগের সঙ্গে ছিল খুব ভাব। মধু গোস্বামীর সঙ্গেও আলাপ। শেখর গাঙ্গুলী আমাদের গ্রামে যাত্রা করতে এসে বাবা ও মালেকভাইয়ের প্রশংসা করে যান। মা খুব রেগে যেতেন। কারণ যাবে সুস্থ শরীরে ফিরবে না খেয়ে না খেয়ে রাত জেগে যক্ষ্মা বাধিয়ে। আমি মুখ দিয়ে রক্ত পড়ার কথা শুনেছি। দেখিনি।এ-সব ১৯৬৬ র আগের গল্প।১৯৮৮ তে পার্টির সদস্যপদ ত্যাগ করে আবার চার মাস যাত্রাদলে কাটিয়ে এলেন।আবার বিচিত্র পেশার গল্পও শুনেছি। পার্টির বই পত্রপত্রিকার বিক্রেতা। আনন্দমেলা নয় কিশোরভারতী পড়াতে হবে। ভূতের গল্প নয় সাহসের বিপ্লবের বিজয় শোনাতে হবে-- এই ইচ্ছা।বিক্রি নামে। ঘর থেকেই টাকা শোধ দিতে হতো।একবার এক ভিডিও হল খুলে ফেললেন যৌথভাবে। ভালো ছবি দেখাবেন কেরলের শাস্ত্রসাহিত্য পরিষদের ধাঁচে।মেহমুদ, দিলীপ কুমার, চার্লি চ্যাপলিন, মেল গিবসনের ছবি দেখাবেন স্বপ্ন।লোকে দেখতে চায় নীল ছবি।চললো না।মাথায় এলো হোটেল করবেন। ভারতের নানা রাজ্যের ভালো খাবার খাওয়াবেন। বাঙালির ডাল ভাত ছাড়াও পুষ্টিকর খাবার আছে-- বোঝাবেন। মা বললেন, যেদিকে দুচোখ যায় চলে যাবো। ঘরের হোটেল একমাস সামলাও, তারপর।মা তো জানেন, জমি যাবে, লাভ কিছু হবে না।একবার ঠিক করলেন, ধান ব্যবসা।একজনকে নিয়ে এলেন, বললেন, এ বড়ো ব্যবসায়ী হবে, দেখে নিও। বাবার পুঁজি তাঁর শ্রম।বাবার দৃষ্টি ভালোই ছিল, বাবার সব পার্টনার বড়োলোক হতো, বাবাকে কেবল আর কয়েক বিঘা জমি বেচতে হতো এই যা।শেষ বয়সে খুব ইচ্ছে হয়েছিল, একটা ট্রাক্টর কেনার।আমি বলেছিলাম, কিনে দেবো।তুই কেন দিবি। দিলেও ধার হিসেবে। সুদ নিতে হবে।পাগল হয়েছো। সুদ নেবো।নিবি, ব্যাঙ্কে রাখলেও তো পেতিস। তিন পার্সেন্ট দেবো।তাহলে তুমি অন্য লোক দেখো। আমি দেবো না।আচ্ছা নেবো। তবে শোধ করে দেবো। নিতে হবে।আচ্ছা দেখা যাবে।তাহলে নেবো নাঠিক আছে আগে তো ভালো হও ঘরে চলো।#বাবার ঘরে ফেরা হলো না।অপারেশন করার দিনেই চলে গেলেন।বারবার ঠকঠক আওয়াজ করে ডাকছিলেন, বাবার সংক্রমণ হয়ে যাবে ভেবে পাশে গেলাম না।আর শোনা হলো না কী বলতে চেয়েছিলেন।বলবে আব্বা?বলবে!১৮.০৭.২০২১Sisir Datta আমাদের প্রিয় শিক্ষক লিখেছেন:ওনার গল্প এত ছোট কিকরে হয়। এই সামান্য কটা লাইনে ওনার কোন গুণমুগ্ধই সন্তুষ্ট হবেন না।Pintu Kumar Majumder শিক্ষক লিখলেনতোমাদের গ্রাম ও কোনা গ্রামের রান্না পূজা তে প্রায় সব নামী যাত্রা অভিনেতা ও অভিনেত্রী এসেছে। কোনা তে যাত্রার সময় এনামুল জেঠু এসে মজুমদার বাড়িতে উঠতেন। আমার বাবা দেহিপদ মজুমদারকে জেঠু খুব ভালোবাসতেন। রতন কোলে, স্বপ্না কোলে, জ্যোৎস্না দত্ত, মিতা দে, জ্যোতি ভট্টাচার্য, বিমল বোস, আরও অনেক দামী শিল্পী কোনা ও তোমাদের গ্রামে গেছেন। রাখাল সিং প্রায় প্রতি বছর যেতেন। উনি ও এনামুল জেঠু আমার মায়ের হাতের তৈরী আমতেল দিয়ে মুড়ি মাখা খুব ভালোবাসতেন। আমাদের কোণা গ্রামের বাড়িতে রান্না পুজোর সময় চাঁদের হাট বসতো। এনামুল জেঠু ভীষণ জ্ঞানী মানুষ ছিলেন। অনেক যাত্রা পালাকার যাত্রা লেখার সময় এনামুল জেঠুর সাথে পরামর্শ করতেন।আমার মনে হয় অনেক বিষয় তোমার জানা নেই, বিশেষত জেঠুর যাত্রাপালার বিষয় সম্পর্কে। শম্ভু বাগ, ভৈরব গাঙ্গুলী, বিমল বোস, শান্তি গোপাল, এদের অনেক যাত্রা গ্রন্থে জেঠুর তথ্য সরবরাহ হয়েছিল। জেঠু খুব ধীর স্থির ও নির্লিপ্ত মানুষ ছিলেন। বেশি নিজেকে প্রকাশ করা পছন্দ করতেন না। রাখাল সিং একবার নিউ গণেশ অপেরা তে "বিরোহী সুলতান" যাত্রা করার আগে বাবা কে নিয়ে এনামুল জেঠুর কাছে বসে চরিত্র সম্পর্কে পাঠ নেন।ক্রীতদাস বলে বিমল বোস এর যে যাত্রা বই আছে তাতে জেঠু তথ্য সরবরাহ করেছিলেন। বাবা এইসব আমাদের সব বলেছিলেন। তুমি যদি আগে বাবার সাথে বসতে তাহলে অনেক কিছু জানতে পারতে। আর উপায় নেই। পরে দেখা হলে আরো বলবো।বোন শাহানারা লিখেছেন:উৎপল দত্ত এর নাটকের গ্ৰুপে সুযোগ পেয়েছিলেন। শুধু ঘড়ি ধরে রিহার্সাল এ যেতে পারতেন না বলে,ভয়ে ছেড়ে দিয়েছিলেন। বাবার মুখে শোনা গল্পটা ছিল এমন– দাদুর বন্ধু তুলসী লাহিড়ী বাবাকে উৎপল দত্ত এর কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন পিতৃপরিচয়ে। দাদু স্টার থিয়েটরে অভিনয় করতেন। রিহার্সালের সময় ছিল বিকেল সাড়ে চারটে। উৎপল দত্ত সময়টা মনে রাখতে বলেছিলেন। বাবা প্রথম দিন ৪.৩৫ নাগাদ গিয়েছিলেন। উৎপল দত্ত বলেছিলেন আমার ৪.৩০ মানে ৪.৩০, ৪.৩৫ নয়। পরের দিন বাবা ৪.৩১ এ পৌঁছান। তাতে উৎপল দত্ত বলেছিলেন– শুধু মাত্র মুশা সাহেব এর ছেলে বলে কিছু বললাম না। সময়টা মনে রেখো। অনেক চেষ্টা করেও বাবা তার পরের দিন ৪.২৯-এও পৌঁছাতে পারেননি বলে ছেড়ে দিয়েছিলেন।@অহমিয়া কবি Pranab Hazarika লিখেছেনওঁনাৰ উপৰে আমি একটা কবিতা লিখেছিলেন ২০১৩ সালে ৷ শ্যাম বাজাৰেৰ বীৰেন্দ্ৰ কৃষ্ণ মঞ্চে অনুস্হিত এক কবি সন্মেলনে ওঁটা পাঠ কৰেছিলাম ৷নিচে কবিতা টি দেওয়া হল : বর্ধমান জেলার এক প্রান্তিক কবি - অভিনেতা জনদরদী এমানুল হক ২০১৩ সালে ইহ সংসার ত্যাগ করেন ৷ ওঁনার স্মৃতিতে একটি কবিতা রচনা করেছিলাম যেটা ১০ - ১১ - ১৩ তারিখে শ্যামবাজার বীরেন্দ্র কৃষ্ণ মঞ্চে আন্তর্জাতিক সাহিত্য সংস্কৃতি দ্বারা আয়োজিত কবি সন্মেলনে পাঠ করেছিলাম ৷৷ মৃত্যু অপরাজেয় ৷ প্রণব কুমার হাজরিকা বিশ্ব মঞ্চে জীবন নাটের চরিত্র রূপায়ণ - মনুষ্য কুলের আগমন, অলিখিত নাট অভিনয় মৃত্যু অবধি ৷তার পর মঞ্চ থেকে প্রস্হানরেখে যায় কতগুলি স্মৃতি ৷আমাদের মধ্যে নাটের মাঝে নাট লেখা হয় - মানুষের জীবন সংগ্রাম , হাসি কান্না, প্রেম ভালোবাসা সাবলীল গতিতে প্রতিফলিত হয় কাহিনীর মধ্য দিয়ে ৷সৃষ্টি হয় নৃত্য কবিতা গীত চিত্র গল্প - জনজীবনের দাপোন ৷ সুন্দরতম শিল্প বহিঃ প্রকাশ ,সে শিল্প প্রাণে জাগরিত জনজীবন ৷হে শিল্পী! সৃষ্টি অনুপ্রাণিত করে জনতাকে, প্রদান করে আনন্দ , পথ নির্দেশনা করে সুন্দর ও সংগ্রামের ৷সেই মৃত্যু অপরাজেয় যার সৃষ্টি রেখে যায় সুন্দর পিপাসু জনতার মাঝে অনুপম মধুর স্মৃতি ৷
জনতার খেরোর খাতা...
হেদুয়ার ধারে - ১৪৪ - Anjan Banerjee | সাগর ফিরে এল প্রায় দশ মিনিট পর। একাই ফিরল। এসে বলল, ' নাঃ ... ফস্কে গেল। শালা কোন গলতা দিয়ে ছুঁচোর মতো হেভি স্পীডে ভেগে গেল বুঝতে পারলাম না ... ঠিক আছে আমি লোক লাগাচ্ছি। কিন্তু চিন্তার ব্যাপার হচ্ছে স্যারের বাড়িটা ওরা মার্ক করে নিয়েছে, যেটা আমি চাইছিলাম না ... 'সুরেশ্বর মল্লিক রীতিমতো অস্থির বোধ করছিল। সে বলল, ' তুমি তো একঝলক মুখটা দেখতে পেয়েছিলে। চেনা লাগল ? '----- ' না, ঠিক বুঝতে পারলাম না। চেনা মুখ নয় ... '----- ' আমরা তা'লে জাতে উঠে গেছি বলতে হবে ... কি বলেন মল্লিকদা ... ইনফর্মার লাগানো হচ্ছে ... কেউ কেউ বেশ গুরুত্ব দিচ্ছে আমাদের ... ' নিখিল ব্যানার্জী বললেন।সুরেশ্বর বললেন, ' হমম্ ... বুঝতে পারছি না শালা আমাকে ফলো করে এখানে এল কিনা ... যাই হোক, এটা নিয়ে আপনি চিন্তা করবেন না ... আমি বের করে ফেলব ঠিক ... '------ ' না না ... চিন্তা করব কেন। আপনাদের ওপর ভরসা না করলে আর কার ওপর ভরসা করব ? আচ্ছা মল্লিকদা, আপনার মতে এই মুহুর্তেআমাদের কোন ব্যাপারটা সবচেয়ে বেশি অ্যাড্রেস করা উচিত ... মানে কোন জিনিসটা সমাজ থেকে দূর করার জন্য সচেষ্ট হওয়া উচিত ? 'নিখিলবাবুর কথা শুনে সুরেশ্বর কি একটু ভাবলেন, তারপর তার নিজস্ব চাঁচাছোলা ভাষায় তার চেনা জগতের কথা বলে উঠলেন, ' আমার মনে হয় নেতাদের পোষা বাঞ্চোত দালালগুলো যারা গরীব ঘরের কচি কচি মেয়েগুলোকে ফুসলে নিয়ে এসে সোনাগাছিতে ঢোকাচ্ছে সেগুলোকে দুরমুশ করার দরকার ... 'বেলাগামভাবে কথাটা বলে ফেলেই মল্লিকবাবু লজ্জায় জিভ কাটলেন।----- ' ওই... ইয়ে ... কিছু মনে করবেন না স্যার ... অনেক দিনের আদত তো ... স্লিপ অফ টাং হয়ে গেল ... এহেঃ... 'নিখিলবাবু স্মিত হেসে বললেন, ' আপনি এত সংকোচ বোধ করছেন কেন সুরেশ্বরবাবু। আপনি আপনার অনুভূতি প্রাঞ্জল ভঙ্গীতে প্রকাশ করেছেন। এতে অন্যায়ের কি আছে। আপনার বক্তব্যে কোন জটিলতা নেই। এভাবে যদি সবাই বলতো অনেক সুবিধা হত। সে যাই হোক, এ ব্যাপারে আপনিই আমাদের রাস্তা দেখান। আপনার কাছে পরামর্শ চাইছি এ ব্যাপারটায় কিভাবে এগোন যায় ... বা আপনার কাছে এমন কোন খবর আছে কি যাতে ইমিডিয়েট অ্যাকশান করার দরকার আছে ?'প্রশ্নটা শুনে সুরেশ্বর মল্লিক বললেন, ' দিন তিনেক বাদে একটা সাপ্লাইয়ের কাজ আছে বলে খবর পেয়েছি। ওই সময়ে অ্যাকশান করতে পারলে কয়েকটা মেয়েকে বাঁচানো যেতে পারে। আমার কাছে খবর আছে .... বনগাঁর দিক থেকে আনা হচ্ছে। শিয়ালদা হয়ে দর্জিপাড়ার দিকে আসবে। নন্দলালের সঙ্গে আমার যোগাযোগ আছে এখনও। তার কাছেই শুনলাম। নন্দ খুব ভাল লোক। সে আনন্দীর ছেলে। আনন্দীর এখন বয়েস হয়ে গেছে। সে এখন আর ঘরে লোক নিতে পারে না। খুব কষ্টে আছে। নন্দ অবশ্য আমার চেয়ে অনেক ছোট। হাজার হোক পুরণো ইয়ার। সহজে কি ছাড়া যায় ... অনেকদিনের সম্পক্ক ... ওখানে আর ভাল লাগে না নন্দলালের। কিন্তু কোথায়ই বা যাবে। জম্ম থেকে ওপাড়াতেই আছে। মহল্লায় নতুন মেয়ে ঢোকালে নন্দর খুব খারাপ লাগে। আমার বাড়িতে এসে ওসব বলে ... আমিই বা কি করব বলুন তো ... ওদের খুব বড় চক্র ... আমারও তো প্রাণের ভয় আছে ... পরিবার নিয়ে থাকি ... 'এতক্ষণ বলার পর সুরেশ্বর দেখলেন নিখিল স্যার তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন।মল্লিকবাবু একটু থতমত খেয়ে গেলেন। বললেন, ' এই ইয়ে ... কিছু মনে করবেন না। ওপাড়ার কথা এখানে বলা ঠিক হয়নি ... আপনারা শিক্ষিত লোক ... মাফ করবেন ... 'নিখিলবাবু একইভাবে তার দিকে তাকিয়ে আছেন দেখে মল্লিকবাবু বললেন, ' দেখলেন তো জানলা দিয়ে দেখে গেল একজন ... আমি এসে আপনাদের ঝঞ্ঝাটে ফেললাম ... ঠিক আছে, বাদ দিন ওসব ... 'এবার নিখিলবাবু বললেন, ' আমি একটা অন্য কথা ভাবছিলাম মল্লিকদা .... '----- ' হ্যাঁ ... কি ? তা, মানে আমার যদি কোন অপরাধ হয়ে থাকে .... '----- ' তোমাকে আমার জন্য একটু কষ্ট করতে হবে.... '----- ' ও ... তা কি ? '----- ' নন্দলালের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। ব্যাস, এইটুকুই। আর কিছু করতে হবে না। কথা আমিই বলব ... ' নিখিলবাবু বললেন।----- ' নন্দলালের সঙ্গে আপনি ... মানে ... '----- ' মানে টানে কিছু নেই। কবে দেখা করাবেন বলুন ... '------ ' ও আচ্ছা ... ঠিক আছে আমি নন্দর সঙ্গে যোগাযোগ করছি ... 'এবার সাগর নীরবতা ভঙ্গ করল।বলল, ' অসুবিধে হলে বল না আমি তোমার সঙ্গে যাব। চিন্তা করছ কেন ? তারপর তুমি যেটা বললে ওই অ্যাকশানের প্ল্যানটা করে নিতে হবে ... দিনটা জানতে পারলে ভাল হত ... '----- ' নন্দর সঙ্গে কথা বললে জানা যেতে পারে মনে হয় ... ' সুরেশ্বরবাবু বললেন।নিখিল ব্যানার্জী বললেন, ' তবে তাই হোক ... ' গুনগুন করে গেয়ে উঠলেন, আমাদের যাত্রা হল শুরু, আসুক অন্ধকার ... বাতাস উঠুক, তুফান ছুটুক ... ফিরব না কো আর ... 'মল্লিকবাবু তার নিজস্ব ভঙ্গীতে বলে উঠলেন, ' হ্যাঁ ... সেটাই সেটাই ... 'এইসময়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে একটা মেয়ে বলল, ' আসতে পারি স্যার ... 'নিখিলবাবু ঘাড় ঘুরিয়ে দরজার দিকে তাকালেন।----- ' আরে কাবেরী আয় আয় ... কি খবর তোর... কফি হাউস থেকে এলি ? '----- ' না স্যার ... চারুলতা দেখে এলাম ... রূপবাণীতে 'কাবেরী ঘরে ঢুকে বসল।----- ' আচ্ছা ... সত্যজিত রায়ের ছবি। ওটা রবীন্দ্রনাথের কোন গল্প থেকে করা জানিস তো ? '----- ' হ্যাঁ স্যার ... নষ্টনীড় '----- ' গুড ... ও গল্পটা থেকে ফিল্ম বানানো মোটেই সহজ কাজ নয় ... জানিনা কেমন হয়েছে ... '----- ' দারুণ স্যার ... দেখে আসুন একদিন সময় করে। একদম সত্যি মনে হবে ... '----- ' হ্যাঁ ... এটাই হল আসল কথা। এই একদম সত্যি মনে হওয়াতেই কোন আর্টের আসল সাফল্য ... মানুষ যদি একাত্ম হতে না হতে পারে তা হলে সেই সৃষ্টি অসফল। সে যাই, তোর কফি হাউসের লোকজনের খবর কি ? অনেকদিন দেখা নেই ... '----- ' হ্যাঁ স্যার ... ওরা, আপনার কথা খুব আলোচনা করে। দু একদিনের মধ্যেই আসবে। ওদের তিনজনের মধ্যেই খুব আর্জ আছে ... '----- ' হুমম্ ... আসতে বলিস, কাজ আছে। '----- ' হ্যাঁ স্যার কালই বলব ... ওদের ম্যাগাজিনের নতুন ইস্যু বেরিয়েছে ... '----- ' তাই নাকি ? দিস তো এক কপি। '----- ' হ্যাঁ ... নিশ্চয়ই ... পরের ইস্যুতে আমিও একটা কবিতা দেব ঠিক করেছি। জানিনা সিলেক্টেড হবে কিনা ... '----- ' তাই নাকি ... তুই কবিতা দিবি ? ইন্ট্রেস্টিং ! '----- ' কবিতাটা লেখা হয়ে গেছে। নিয়ে এসেছি স্যার ... শোনাব ? '----- ' নিয়ে এসেছিস ? পড় পড় ... 'এইখানে সুরেশ্বর মল্লিক একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। এসব কবিতা টবিতা তার চেনা জগতের বস্তু নয়। তিনি বললেন, ' আচ্ছা ... স্যার, আমি তা'লে এখন উঠি। দেখি গিয়ে নন্দর সঙ্গে কথা বলা যায় কিনা .... 'নিখিলবাবু বাধা দিলেন।----- ' আরে আরে ... যাবেন'খন। কাবেরীর কবিতাটা শুনে যান না ... নইলে কষ্ট পাবে ও ... নে পড় ... 'কাবেরী তার ঝোলা ব্যাগ থেকে একটা ডায়েরি বার করে সেটা খুলে পড়তে লাগল ----পথে ঝলসায় রোদ্দুর গনগনেইস্পাত কাটা ধারাল শোনিত স্রোতেওলটপালট সাইক্লোন মারে ঝাপটাঘাম ও রক্ত মাখামাখি অদ্ভুত।পৌঁছে যাবই মোহনায় নিশ্চয়জাহাজ যেখানে বেঁধে রাখা আছে পোক্তনিয়ে যাবে বলে অচেনা দ্বীপের কোলেজলে দোল খায় পাগলের মতো অস্থির।এস সকলে পথ হাঁটি বহু ক্রোশদিগন্ত মোরা ছুঁয়ে ফেলতেও পারিছোঁয় না মোদের কখনও মরণ ভয়শামিল হয়েছি নভচর ঈগল উড়ানেআকাশ চুম্বী গিরি শৃঙ্গ কানায়।শয়তানদের মোরা ছাড়ব না কিছুতেইকতবার বল পারবি হারাতে আমাদেরআমরা তোদের ধ্বংস নামিয়ে আনবইরাষ্ট্র ছাড়াই রাষ্ট্রকে দেব কুর্নিশনতুন দলেরা গড়বে আর একটা দেশ।কাবেরী বলল, ' আর একটু হবে। এখনও কমপ্লিট হয়নি। কেমন হচ্ছে স্যার ? 'স্যার বললেন, ' তুই তো আমাকে অবাক করলি রেকাবেরী ... তোর ভেতরে এত কিছু ছিল জানতেই পারিনি। লেখাটা কমপ্লিট কর, তারপর আবার শুনব। গুণী মানুষের দেখা পেলাম যাহোক ... 'কাবেরী লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে গিয়ে বলল, ' কি যে বলেন স্যার ... 'তারপর বলল। ' এছাড়া আর একটাও লিখেছি। সেটা রোমান্টিক কবিতা। আজকে আনিনি। পরের দিন নিয়ে আসব।'স্যার বললেন, 'অবশ্যই অবশ্যই ... রোমান্টিক কবিতা আমার খুব প্রিয় ... 'কাবেরী মনে মনে ভাবল, ' তাই বুঝি ? দেখে তো মনে হয় না ... 'মল্লিকবাবু বললেন, ' আমি তাহলে এবার আসি .... খবর দেব ... 'সাগর বলল, ' চলুন আমিও যাব ... 'সে উঠে দাঁড়াল। তারপর নিখিলবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, ' কোর কমিটির সদস্য বেড়ে যাবে মনে হচ্ছে স্যার ... কাকে রাখবেন, কাকে ফেলবেন ... 'নিখিলবাবু হেসে ফেললেন। বললেন, ' দেখ কি করবে। তবে, সব সদস্যই যেন কোর কমিটির না হয়ে যায় ... আধিপত্যবাদের সূচনা এর থেকেই সৃষ্টি হয় ...----- ' তাই তো ... আচ্ছা আসি এখন ... ' ( চলবে )********************************************আষাঢ়ষ্য প্রথম দিবসে.. - Kasturi Das | আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে..কলম যেখানে মেঘ-বৃষ্টির বন্দনাগীত গাইবে বলে রেডি, ঠিক সেই মোক্ষম মুহূর্তে মিস্টার কাক্বেশ্বরের ভয়ানক মনখারাপ। বিরহে সপ সপ করছে মন। ঝরঝর করে জল গড়িয়ে পড়ছে চোখ দিয়ে। মেঘ কতো করে বোঝালো। বৃষ্টি সুন্দর নৃত্যগীত পরিবেশন করলো। কিন্তু নাহ, কোথায় কী ! ভগ্নহৃদয়ে, চোখের জল আড়াল করতে উড়ে গিয়ে বসলো টং কাকুদের বাড়ির একদম টপ এ।কী করবে বল..ওর বউ পালিয়েছে। ঘর শূন্য। ছানাপানারাও এই কিছুদিন হলো, যে যার পথে। এতদিন ওদের খাওয়ানো, উড়তে শেখানো, চোখে চোখে রাখা..সব তো ওরা দুজনেই করতো। কাক মেসো আর কাকী পিসী। বেশ চলছিল। হঠাৎ কী যে হলো !!..বাচ্চারা একটু উড়তে শিখতেই ও খেয়াল করেছিল, কাকী র কোনোদিকে মন নেই। কেমন যেন উড়ু উড়ু ভাব। কিছুদিন হলো আম গাছের পাঁচতলার ব্যালকনিতে একটা single ফান্টুস এসেছে। সারাক্ষণ ঘাড় কাত করে style মারে। ওই --- শিওর ফুসলেছে কাকী কে। নয়তো.. গতপরশু দিনেও তো বড়াই বুড়ির বাড়ির ছাদের কার্নিশে বসে কতক্ষণ ধরে বিলি কেটে দিল মাথায়। তখনো বুঝতেই পারেনি যে এমনটা হতে পারে!!যাক, থানা পুলিশ করে লাভ নেই। বরং লিফলেট ছাপিয়ে সাটিয়ে দেবে গোটা আমগাছের গায়ে। পাঁচতলা থেকে একতলা। নাম- কন্দ সুন্দরী কাকী বয়স- আনুমানিক ১২ গায়ের রঙ- উজ্জ্বল কালো পাখার পালক- ডানদিকে ছেঁড়াবন্ধুরা, সন্ধান থাকলে জানিও কিন্তু প্লিজ। ওকে না পেলে, এমন মেঘমন্দ্রিত আষাঢ় - হৃদয়ের জলে ভেসে যাবে যে !!...(মেঘমন্দ্রিত আষাঢ়ের অপেক্ষাতে কত দিন কাটবে কে জানে!!!)নইপলের ভারতকে অস্বীকার এবং পুনরাবিষ্কার - পাপাঙ্গুল | ত্রিনিদাদ নিবাসী দ্বিতীয় প্রজন্মের ভারতীয় বিদ্যাধর সূরজপ্রসাদ নইপল ছোটবেলা থেকেই হিন্দু আচার, ভারত ইত্যাদি শুনে শুনে চাক্ষুষ করতে আগ্রহী। ভারতে তিনবার ঘুরতে এসেছিলেন - ১৯৬২, ১৯৭৫ এবং ১৯৮৯ সালে। অর্থাৎ তিন দশকে ভারতের পরিবর্তন তার চোখে ধরা পড়ে। এই বইগুলি ভ্রমণকাহিনী কম, ভারতের সমাজ, রাজনীতি ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে ভাষ্য বেশি বলাই যুক্তিসংগত হবে। তৃতীয় বইটিকে বিশেষ করে বিবিধ চরিত্রের গ্যালারি এবং তাদের দীর্ঘ ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক ইতিহাসের সাক্ষ্য বলে মনে হয়।পিতামহ ভারতের উত্তরপ্রদেশের পূর্বাঞ্চলের যে গোরখপুর গ্রামে থাকতেন, সেখানে সবাই ছিল দুবে অথবা তিওয়ারি। সবাই ব্রাহ্মণ এবং পরস্পরের লতাপাতায় আত্মীয়। অল্প বয়সে নৈপলের পিতামহ সেই গ্রাম ছেড়ে বেনারসে গেছিলেন পড়াশুনো করতে। গরীব সেই গ্রামে হয়ত একবার দুর্ভিক্ষ হল। এক আড়কাঠি তাকে বোঝায় বহুদূরে ত্রিনিদাদ নামের দেশে শ্রমিকরা আছে, কাজ করছে। তারা পন্ডিত এবং পুরোহিত চায়। অন্যসময় হলে তাকে হয়ত ঢিলিয়ে মেরে ফেলা হত। দুর্ভিক্ষের সময় বলে পাঁচ বছরের জন্য তিনি চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন এবং ত্রিনিদাদ পৌঁছোনর পর যথারীতি সেখানে টোল খোলেননি, চিনির কারখানায় কাজ করতেন। ঘর, খাবার এবং মজুরি পেতেন। রাতের বেলা যজমানি। বেনারস ফেরত পুরোহিতের চাহিদা ছিল ত্রিনিদাদে। কারখানার সাহেব একদিন তাকে বললেন - 'তুমি পন্ডিত। আমাকে সাহায্য করতে পারবে? আমি এক ছেলে চাই।" অতঃপর নৈপলের পিতামহ সাহেবের স্ত্রীকে এক ক্ষেত্ৰজ পুত্র উপহার দিলেন। খুশি হয়ে সাহেব সমস্ত আখ গাছ শুদ্ধ তিরিশ বিঘা জমি দিয়ে দিলেন পিতামহকে। প্রথম বইতে নইপলকে একজন ভয়ার্ত পর্যটক বলে মনে হয় -I had seen photographs of the Punjab massacres of 1947 and of the Great Calcutta Killing; I had heard of trains – those Indian trains! – ferrying dead bodies across the border; I had seen the burial mounds beside the Punjab roads. Yet until now I had never thought of India as a land of violence.এছাড়াও নইপলকে খুব বিরক্ত বলে মনে হয়, কারণ তিনি নানাবিধ হিসেব মেলাতে পারছেন না। তার ভারতীয় ইংরেজিকে একরকম অক্ষম নকল বলে মনে হতে থাকে। এংলো ক্লাব , সাহেব চাপরাশি ইত্যাদি নিয়ে বহু কৃত্রিমতা। ভারতে বক্সওয়ালা [সমাজের ওপর তলার মানুষ যারা সরকারি অথবা বৃটিশ কোম্পানিতে কর্মচারী ছিলেন] দের জীবন যেন অতিরঞ্জিত একরকমের বৃটিশ রূপকথা যা ইংল্যান্ড ধ্বংস হয়ে গেলেও বেঁচে থাকবে। To be English in India was to be larger than life.These boxwallahs represented in their own eyes a synthesis of Indian and European culture. They were admired and envied by Indians outside the group because their boxwallah jobs were secure, in addition to being, with the British connection, a badge of breeding.England of the Raj. This still lived. It lived in the division of country towns into ‘cantonments’, ‘civil lines’ and bazaars. It lived in army officers’ messesএছাড়াও Indians defecate everywhere. for it is said that the peasant, Muslim or Hindu, suffers from claustrophobia if he has to use an enclosed latrine.ফলে, নইপলের মনে একরকম বিচ্ছিন্নতা জন্মায় তার শিকড় বলে যাকে ছোটবেলা থেকে জেনে এসেছেন সেই দেশের প্রতি। Colonial India I could not link with colonial Trinidad. Trinidad was a British colony; but every child knew that we were only a dot on the map of the world, and it was therefore important to be British: that at least anchored us within a wider system. It was a system which we did not feel to be oppressive; and though British, in institutions and education as well as in political fact, we were in the New World, our population was greatly mixed, English people were few and kept themselves to themselves, and England was as a result only one of the countries of which we were aware.I was not English or Indian; I was denied the victories of both.বোম্বাই বন্দরে জাহাজ থেকে নামার পর ট্রেন ধরে দিল্লি, সেখান থেকে পাঠানকোট। সেখান থেকে শ্রীনগর। রাস্তায় অবন্তীপুরের ধ্বংসাবশেষ। হরি পর্বতের ওপর আকবরের বানানো কেল্লা। অন্যদিকে শঙ্করাচার্য পাহাড়। হজরতবাল মসজিদ। বাটের মতো বহু কাশ্মীরি পদবী এখনো হিন্দুদের, অথচ হিন্দু হবার কোনো স্মৃতি তাদের মনে নেই। পাহাড়ে থাকে গুহা মানুষরা, যাদের দেখে নইপলের মধ্য এশিয়ার ঘোড়সওয়ার দের উত্তরসূরী মনে হয়। সমতলের কাশ্মীরিরা তাদের ঘৃণা করলেও গরমকালে খচ্চর নিয়ে তারা সমতলে নেমে আসে। উপত্যকায় সবথেকে ভারত বিরোধী হল পাঞ্জাবি মুসলিমরা। U.N. ছাপ মারা জীপ আর স্টেশন ওয়াগনেরা যুদ্ধবিরতি সীমা কেউ লঙ্ঘন করছে কিনা সেটা নজরে রাখে। রেডিও পাকিস্তানের শব্দ ভেসে আসে বেতারে। নইপল ঘুরে বেড়াতে থাকেন পান্ড্র্রেথান মন্দির এবং পহেলগামের সূর্যমন্দিরে। একসময় কাশ্মীরের মহারাজ করন সিং বললেন অমরনাথ যাত্রায় যেতে। যাত্রাপথে একটি বিদেশী মেয়ের সঙ্গে আলাপ হয় যে রাজাগোপালাচারীর লেখা মহাভারতের ওপর একটি বই পড়তে ব্যস্ত অথচ পরে এক কাশ্মীরি মুসলিমকে বিয়ে করে ফেলে। পশ্চিম ইন্ডিজের ভূগোল যথেষ্ট পুরোনো হলেও বৃটিশ সাম্রাজ্য 'নতুন'। ত্রিনিদাদ ছিল সমুদ্র সাম্রাজ্যের অংশ আর এদিকে ওদিকে একটা বন্দর একটা বাজার ছাড়া কিছু স্থাপত্য ছিল না। ১৮০০ জনসংখ্যার ত্রিনিদাদে কোনো 'ইতিহাস' ছিল না। উল্টোদিকে ভারতের ক্ষেত্রে -It is like reading of a land periodically devastated by hordes of lemmings or locusts; it is like turning from the history of a coral reef, in which every act and every death is a foundation, to the depressing chronicle of a succession of castles built on the waste sand of the sea-shore.This is Woodruff on the difference between European history and Indian history.It is a history whose only lesson is that life goes on. There is only a series of beginnings, no final creation. The sandcastle is flattened by the tide and leaves no trace, and India is above all the land of ruins.নইপলের চোখে ভারত একটি অঞ্চল যেখানে বারবার লুঠ করা যায়, করা হয়েছে। যেখানে নিজের বিজয়কে স্মরণীয় করে রাখতে বিজেতারা এক একটি স্মারক বানিয়েছে পাঁচশো বছর ধরে , আবার কেউ এসে তা ভেঙে দিয়েছে। ফলে সব মিলিয়ে বিষয়টি ব্যক্তিগত ইতিহাস এবং সামগ্রিক হিসেবে কোথাও পৌঁছতে পারেনি। এখনো ভারত নিজের ইতিহাসকে ইউরোপের চোখ দিয়ে দেখছে। In any clash between post-Renaissance Europe and India, India was bound to lose.*The stupefaction of people is one of our mysteries. At school in Trinidad we were taught that the aboriginal inhabitants of the West Indies ‘sickened and died’ when the Spaniards came.অথচ একই সঙ্গে নইপল স্বীকার করতে বাধ্য হন ভারত পেরু বা মেক্সিকোর মত শুকিয়ে যায়নি। হিন্দু ভারত বিজেতাদের নিজেদের অংশ করে নিতে পেরেছে। প্রথমদিকে বৃটিশরা ভারতে স্বাগত ছিল। মুঘলদের মত বৃটিশরা বলেনি যে পৃথিবীতে স্বর্গ থাকলে তা এখানেই। ভারত শাসন করার সময় তারা এই চিন্তাকেই অবজ্ঞা করেছে এবং ইংল্যান্ডকে প্রোজেক্ট করেছে তাই ভারতবাসীরা বৃটিশদের অনুকরণে তৈরী একটি জাতীয়তাবাদকে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। In the acquiring of an identity in their own land they became displaced. It is part of the mimicry of the West, the Indian self-violation.*If I had read Camus’s The Rebel before writing this chapter, I might have used his terminology. Where Camus might have said ‘capable of rebellion’ I have said ‘positive’ and ‘capable of self-assessment’; and it is interesting that Camus gives, as examples of people incapable of rebellion, the Hindus and the Incas. এই বইতে নইপল কিছু ভারতীয় ইংরেজি লেখক যেমন আর কে নারায়াননের প্রশংসা করেছেন - He seems forever headed for that aimlessness of Indian fiction – which comes from a profound doubt about the purpose and value of fiction – but he is forever rescued by his honesty, his sense of humour and above all by his attitude of total acceptance. He operates from deep within his society. Some years ago he told me in London that, whatever happened, India would go on. নইপলের ভারত ভ্রমণ কালেই এক সপ্তাহের জন্য চীন ভারত আক্রমণ করে। শিকড়হীন অবস্থায় ঝুলে থাকা থেকে নইপল কিছুটা মুক্তি পান যখন তিনি তার পূর্বপুরুষের গ্রামে ফিরে যান এবং সবাই তাকে চিনতে পারে। Customs are to be maintained because they are felt to be ancient. This is continuity enough; it does not need to be supported by a cultivation of the past, and the old, however hallowed, be it a Gupta image or a string bed, is to be used until it can be used no more.India had not worked its magic on me. It remained the land of my childhood, an area of darkness; like the Himalayan passes, it was closing up again, as fast as I withdrew from it, into a land of myth; it seemed to exist in just the timelessness which I had imagined as a child, into which, for all that I walked on Indian earth, I knew I could not penetrate.India is for me a difficult country. It isn’t my home and cannot be my home; and yet I cannot reject it or be indifferent to it; I cannot travel only for the sights. I am at once too close and too far.এমার্জেন্সির সময় নইপল পুনরায় ভারতে আসেন কিছুদিনের জন্য, এই দ্বিতীয় বইতে জোর দিয়েছেন গান্ধী পরবর্তী ভারতে নানারকম ক্ষত সারিয়ে ওঠার চেষ্টার ওপর।এই সফরে তুঙ্গভদ্রা তীরে বিজয়নগরের মালেশ্বরম মন্দির দেখে নইপলের মনে পড়ে বিজয়নগরের ক্রীতদাস বাজার ছিল, দেবদাসী ছিল, সতীপ্রথা প্রচলিত ছিল। বইতে এক ভারতীয় মেয়ের কথা আছে যে বিয়ে করে বিদেশে চলে যায়। অথচ সে ভারতকে ছেড়ে যেতে পারে না কারণ ওই নতুন জায়গায় তার নিজস্ব কোনো পরিচয় নেই। সে এক শূন্যতার মধ্যে বসবাস করে। বেঁচে থাকতে গেলে ভারত এবং নিজের পরিবারের আশ্বাস তার প্রয়োজন তাই সে যখন ইচ্ছে দেশে চলে আসে। Like a sleepwalker, she moved without disturbance between her two opposed worlds.এমার্জেন্সিতে একরকম 'ক্লিন আপ' হয়েছিল। জয়পুরের প্রাক্তন মহারানীকে কর ফাঁকি দেবার অভিযোগে বিনা বিচারে জেলে ভরা হয়েছিল। গ্বলিয়রের রাজবাড়ি ঢুঁড়ে ফেলা হচ্ছিল গুপ্তধনের খোঁজে। বোম্বেতে সরকারি কর্মচারী, ব্যাংকের মাথা, ব্যবসায়দের ফ্ল্যাট তল্লাশি হচ্ছিল কালো টাকার খোঁজে। ১৯৭১ সালে ইন্দিরা গান্ধী দারিদ্রকে রাজনৈতিক বিষয় করে তুলেছিলেন এবং ভোটের সময় আওয়াজ তুলেছিলেন - গরিবি হটাও। অথচ অত্যাচার , দারিদ্রের মতই চিরকাল ভারতে ছিল। এই এমার্জেন্সির সময় যেন নতুন করে সবাই আবিষ্কার করল। উল্টোদিকে বিরোধীরা আওয়াজ তুলেছিল - ইন্দিরা হটাও। জোরালো বিরোধী দল হিসেবে গোমাতার পুজো করে ধীরে ধীরে জন সংঘের উত্থান হচ্ছিল। প্রধান রাজনীতিবিদরা সকলেই নিজেদের মত করে গান্ধীবাদী এবং সকলেরই ভিন্ন ভিন্ন রামরাজ্যের ধারণা আছে। বিজয় তেন্ডুলকরের 'সখারাম বিন্দে' নাটক ১৯৭২ সালে সেন্সর করা হয়। কিছুদিন আগে বিজয় নেহেরু ফেলোশিপ পেয়েছেন যাতে তিনি সারা দেশ ঘুরে হিংসার ওপর কিছু লিখতে পারেন। তেলেঙ্গানা, বিহার এবং পশ্চিম বঙ্গ ঘুরে সেই বই লিখছেন নকশাল আন্দোলনের ওপর। তেন্ডুলকরের পশ্চিমবঙ্গের নকশাল নিয়ে 'কালী কাল্ট' তত্ত্ব - যে আসলে ওখানকার নকশালরা মাওকে শুধু বলি দেবার ব্যাখ্যা করতে ব্যবহার করেছিল।even for a writer like Tendulkar, the discovery of India could be like the discovery of a foreign country.বোম্বেতে এক লক্ষ লোক ফুটপাথে ঘুমোয়। শলে এক একখানা ঘরে আটজন করে ঘুমোয়। এমনকি বিছানা শিফটেও ভাড়া পাওয়া যায়। শিব সেনা এইসব জায়গায় নিজেদের সংগঠনকে জোরালো করে তুলছে। Caste and clan are more than brotherhoods; they define the individual completely. The individual is never on his own; he is always fundamentally a member of his group, with a complex apparatus of rules, rituals, taboos.একই রকম ভাবে নইপল ইউ আর অনন্তমূর্তির 'সংস্কার' বইটি নিয়েও কথা বলেছেন। যে বইয়ে একজন ব্রাহ্মণ তার পরিচয় হারিয়ে ফেলে। India blindly swallows its past. To understand that past, it has had to borrow alien academic disciplines;গান্ধীজির এক প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন যমুনালাল বাজাজ। ১৯৪৮ র পর বাজাজের স্ত্রী বিনোবা ভাভের পৃষ্ঠপোষকতা শুরু করেন। বাকিরাও তাকে গান্ধীজির উত্তরসূরি মনে করতে শুরু করে। Gandhi was made by London, the study of the law, the twenty years in South Africa, Tolstoy, Ruskin, the Gita. Bhave was made only by Gandhi’s ashrams and India. প্রথম দুই বইতে নইপলকে খুবই বিভ্রান্ত মনে হয়, ভারত যেন একটি ধাঁধা যার উত্তর তিনি একজন বহিরাগত হিসেবে কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছেন না। It seems to be always there in India: magic, the past, the death of the intellect, spirituality annulling the civilization out of which it issues, India swallowing its own tail. পঁচাত্তরের এমার্জেন্সির সময় বোম্বের মত শহরে মাফিয়ারা চোরাচালান ছেড়ে বাড়ি বানানো শুরু করে। তারা মানুষকে 'উৎসাহ' দিত, যাতে তারা জমি ছেড়ে চলে যায় এবং সেই জমিতে বাড়ি তোলা যায়। দালাল স্ট্রিটের জৈন ট্রেডার নইপলকে ভারতে ব্যবসার হাল হকিকত বোঝান। তার কথায় অম্বানী প্রথম ধরে ফেলেন পলিয়েস্টার ভারতের জন্য আদর্শ, কারণ মানুষ বেশি জামাকাপড় কিনতে পারে না। This man Ambani goes one step ahead. He makes and breaks policies for himself. Now he sees a demand for polyester. So he gets into polyester, and he makes sure that nobody else is involved in it. After this he takes the next step – making the raw material for polyester. Then he wants other people to make polyester so they can use his raw material.নইপল ১৯৮৪ দাঙ্গা পরবর্তী ধারাভির বসতির মত বোম্বাইয়ের অলিগলি ঘুরে বেড়ান। কথা বলেন শিবসেনা নেতাদের সঙ্গে, বোম্বের ছবিতে গল্প লিখিয়ের কাজ করা বাঙালির সঙ্গে। মুসলমান ডন যে ভবানী শংকরের পুজো দেয়। শিবসেনা নেতার ঘরে দিনেশ্বরী, তুকারাম, একনাথের মত ধ্রুপদী মারাঠা শিক্ষকদের বই রাখা থাকে। When there are riots, you don’t know the meaning of sleep. You can’t sleep. It’s a big sin if someone of your faith is assaulted and you do nothing about it.’এত সব ঘোরাঘুরি এবং কথাবার্তার ফলে -My vision of Bombay began to change: the ‘poor’, the people down there, were acquiring individuality and had begun to stake their own claim to the city; piety (or rage at their condition, or disgust) was no longer a sufficient response.নৈপলের সঙ্গে 'দলিত প্যান্থার' দলের নেতা এবং কবি নামদেও ধসালের পরিচয় হয়। পুনের কাছে এক গ্রামে নামদেও ধসালের বেড়ে ওঠা, যেখানে কড়া ছোঁয়াছুঁয়ি ছিল এবং উঁচু জাতের সঙ্গে জল ব্যবহার নিয়ে মারামারি। বোম্বে থেকে নইপল চলে যান গোয়াতে। ইউরোপ থেকে ছমাসের জলপথের দূরত্ত্বে পর্তুগিজরা গোয়াকে স্প্যানিশদের মেক্সিকোর মত নতুন বিশ্বের শূন্যতা দিয়ে ভরতে চেয়েছিল, পারেনি। পর্তুগিজ ভাষার 'লুসিয়াদ' মহাকাব্যের রচয়িতা কামিওনসের (১৫৭২ ) মূর্তি ছিল একদা পুরোনো গোয়ার কেন্দ্রে। এখন সেখানে গান্ধীজির মূর্তি। গোয়ার পর নইপলের ব্যাঙ্গালোর এবং মাদ্রাজ যাত্রা। রাস্তায় দেখেন আয়াপ্পা তীর্থে [সবরীমালা] চলেছে শুধু কালো পোশাক পরিহিত পুরুষেরা। আয়াপ্পার যারা তীর্থ করতে যান, তাদের আয়াপ্পার বন্ধু বাবরকেও সম্মান জানাতে হয়। কর্ণাটক এবং তামিলনাড়ুতে গিয়ে নইপল দক্ষিণী ব্রাহ্মণ দের জাত রাজনীতিতে ঢুকে পড়েন। কর্ণাটকের এক মন্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়। Power came from the people. The people were poor; but the power they gave was intoxicating. As high as a man could be taken up, so low, when he lost power, he could be cast down.মাদ্রাজের ব্রাহ্মণ এলাকা মাইলাপোর, ত্রিপলিকেন এবং সেখানকার হাজার বছর পুরোনো পার্থসারথি মন্দির। নইপল দক্ষিণ ভারতে দুরকমের হোটেল দেখতে পান - ব্রাহ্মণ হোটেল এবং মিলিটারি হোটেল [যেখানে আমিষ পাওয়া যায়] The average aspiration of the Indian is to grow under a shadow – and this is all right as long as someone else throws the shadow.শিকড় থেকে বিচ্যুত হলে এক একটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠী কিভাবে ধ্বংস হতে পারে, সে বিষয়ে নইপলের বক্তব্য -first the language going, then the reverence for the rituals and the need for them (the rituals going on long after they had ceased to be understood), leaving only a group sense, a knowledge of family and clan, and an idea of India in the background, an idea of India quite different (more historical, more political) from the India that had appeared to come with one’s ancestors.এছাড়াও নইপল দ্রাবিড় আন্দোলনের নেতা পেরিয়ার সম্পর্কে জানতে পারেন। নাস্তিক এবং যুক্তিবাদী পেরিয়ার হিন্দু দেবতাদের নিয়ে মজা করতেন। জাতপাত মানতেন না, ব্রাহ্মণ্যবাদ এবং সংষ্কৃত ভাষা বর্জন, জাত এবং উত্তর ভারতীয় সংস্কৃতি বর্জনের ডাক দিয়েছিলেন, বর্তমান ডি এম কে যে আন্দোলন থেকে উদ্ভূত। হিন্দুদের পুড়িয়ে ফেলা হয় কিন্তু মৃত্যুর পর তার কথামত পেরিয়ার থিরালে তাকে সমাধিস্থ করা হয়েছিল। তার ঘরের ছোট আলমারির ভেতরে নই পল দেখতে পান গৌতম বুদ্ধ এবং লেনিনের ছোট মূর্তি। ভারতীয় সংবিধান পোড়ানোর অভিযোগে পেরিয়ারের ১৯৫৭ সালে ছ মাস জেল হয়েছিল। এরপর নইপল যান কলকাতায় - The British had built Calcutta and given it their mark. And – though the circumstances were fortuitous – when the British ceased to rule, the city began to die.চিদানন্দ দাশগুপ্তর সঙ্গে নইপলের পরিচয় হয় [একদা বক্সওয়ালা ছিলেন]। Chidananda heard Tagore, nearly eighty, deliver a talk in the Shantiniketan temple on ‘Crisis in Civilization’. In that talk – a famous talk, published a few months after Chidananda heard it – Tagore said he had always believed that ‘the springs of civilization’ would come out of ‘the heart of Europe’. Now, with the war and the coming cataclysm, he could no longer have that faith. The calamity Tagore hadn’t foreseen was the calamity that was to come to Calcutta.Communism in Bengal had a long history. It was another colonial import, one of the things that had come after the New Learning of the 19th century, and the mixed cultureপ্রাক্তন নকশাল, বর্তমানে এক কলেজে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপকের সঙ্গে নইপলের বিশদে আলোচনা হয়। ‘রেড গার্ড একশন’ অনুযায়ী যে গ্রামে গেছিল কিন্তু খারাপ জলের আমিবায়োসিস আর স্ক্যাবিসের ভয়ে শহরে ফের চলে আসে। একসময় পার্টি খতমের লাইন নেয়। ধরা পড়ার পর জেল থেকে পিটিশনে সই করে লন্ডনে তার রিসার্চ করতে চলে যাওয়া, পুলিশ সঙ্গে করে প্লেনে তুলে দিতে গেছিল। By 1973 the Marxist-Leninist camp was divided into 20 factions. police and their gangs had killed several thousands.The unions represent what ultimately the true Bengali is like: he is indolent, doesn’t want to work, but he wants something for nothing, and he must protect his dignity at all costs. He will publicly despise the Marwari trader, but he wouldn’t be able to do the same job himself.The only section of people here who seem to be thriving in Calcutta are the Marwaris. They thrive by being middlemen, buying and selling.Perhaps when a city dies the ghost of its old economic life lingers on.লখনৌর এক মুসলিম যে দেশভাগের সময় পাকিস্তানে চলে গেছিল আবার ফেরত চলে আসে কারণ -It was just the wretched laws, hanging like a cloud over one: the call to prayers, the moulvi coming to my friend’s house and asking why he hadn’t seen us at the mosque recently. The thought police. Islam on wheels.রাসেলের কাইজারবাগ লুঠ , বিদ্রোহের সময়ের রেসিডেন্সি। লখনৌ থেকে নইপলের আবার দিল্লি যাত্রা, ‘ওমেন্স এরা’ কাগজের সম্পাদকের সঙ্গে কথোপকথন ইত্যাদি।সাম্প্রতিক ভিন্দ্রেনওয়ালে এবং অপারেশন ব্লু ষ্টার নিয়ে নইপলের অনুসন্ধান করার জন্য গুরতেজের সঙ্গে কথাবার্তা। একবার জেলে গরিব কয়েদির মৃত্যু হয়েছিল পুলিশি অত্যাচারে, কিন্তু গুরতেজকে ম্যাজিস্ট্রেট থাকাকালীন তদন্ত করতে দেওয়া হয়নি, উল্টে যে খুনি তার পদোন্নতি হয়েছিল। অথবা একবার না খেতে পেয়ে মারা গেছিল একটি পরিবার, কিন্তু ডি এম এবং কালেক্টর গুরতেজকে বলেছিলেন সেটা লিখলে হইচই পড়ে যাবে অতএব অন্য কিছু লিখতে হবে।কপূর সিংয়ের অনুকরণে গুরতেজ সিং একসময় আই এ এস থেকে পদত্যাগ করেন।পাঞ্জাবের হিন্দু ছাপাখানা নিয়ন্ত্রণ করত আর্য সমাজ, যারা প্রতিনিয়ত শিখ বিরোধী লেখাপত্র ছাপত। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে মুক্তি বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া শাবেগ সিং ভিন্দ্রেনওয়ালের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। এতকিছুর পর নইপল আবার শ্রীনগরে ফিরে যান সাতাশ বছর বাদে, আজিজের সঙ্গে দেখা করেন। In 27 years I had succeeded in making a kind of return journey, shedding my Indian nerves, abolishing the darkness that separated me from my ancestral past.But there was in India now what didn’t exist 200 years before: a central will, a central intellect, a national idea. The Indian Union was greater than the sum of its parts; and many of these movements of excess strengthened the Indian state, defining it as the source of law and civility and reasonableness.The mutinies were not to be wished away. They were part of the beginning of a new way for many millions, part of India’s growth, part of its restoration.কিন্তু শেষপর্যন্ত নইপল নিজের পরিচিতিকে আর খুঁজে পেলেন কোথায়? একজন বহিরাগত হিসেবেই থেকে গেলেন কি? নইপল নিজেই বলেছেন ভাষা ভারতীয় গোষ্ঠীগুলির প্রধান জোরের জায়গা, কিন্তু সব জায়গাতেই বাধ্য হয়ে দোভাষীর সাহায্য নিতে হয়েছে তাকে। এই তিন বইতে আসলে লুকিয়ে আছে বহু অনাবাসী ভারতীয় ডায়াস্পোরার প্রথম, দ্বিতীয় প্রজন্মের ভারত সম্পর্কে, নিজেদের শিকড় সম্পর্কিত ধোঁয়াশা। নইপল নিজের মত করে সেই ধোঁয়াশা কাটাতে চেষ্টা করেছেন , অথচ ইংল্যান্ডের একদা পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্যের প্রতিনিধি হিসেবে পাশ্চাত্যের চশমা দিয়েই ভারতকে দেখেছেন। তৃতীয় বইতে নইপলের ভারত সম্পর্কিত সুর যেন অনেকখানি নরম, যেন নইপল এতদিনে বুঝে গেছেন তার সঙ্গে এই দেশের নাম জুড়ে যাওয়াই ভবিতব্য। এবং এই ভবিতব্যকে তিনি মেনে নিয়েছেন। এই আইডেন্টিটি রাজনীতির যুগে, ঋষি সুনকের মত 'ভারতীয় বংশোদ্ভূত' রা যখন ক্ষমতার কেন্দ্রে চলে আসেন, তখন এই বইগুলি নতুন ভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। [শেষ] [লেখার শিরোনাম একটি প্রকাশিত নিবন্ধের বইয়ের অনুকরণে দেওয়া]
ভাট...
 অরিন | থাকলে ভাল হয় । "ফিচার রিকোয়েস্ট" ।
অরিন | থাকলে ভাল হয় । "ফিচার রিকোয়েস্ট" । lcm | অরিন, না, কমেন্ট অফ করার উপায় তো নেই। মানে ইউজারের কাছে নেই।
lcm | অরিন, না, কমেন্ট অফ করার উপায় তো নেই। মানে ইউজারের কাছে নেই। lcm | আরে আবাপ বলেছে, তাহলে ভাবুন :-) ডলারে আস্থা নেই, আমেরিকার সঙ্গে ৫০ বছরের চুক্তি বাতিল করল ধনী ‘বন্ধু’ দেশ! বিপদে ওয়াশিংটন?
lcm | আরে আবাপ বলেছে, তাহলে ভাবুন :-) ডলারে আস্থা নেই, আমেরিকার সঙ্গে ৫০ বছরের চুক্তি বাতিল করল ধনী ‘বন্ধু’ দেশ! বিপদে ওয়াশিংটন?
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালকি কিনি, কেন কিনি - সুকান্ত ঘোষ
১৭ জুন ২০২৪ | ৭ বার পঠিত১৯৬৩ সালের কথা – “স্টেট মিউচ্যুয়াল লাইফ ইনসিওরেন্স অব আমেরিকা” কোম্পানী তখন সবে অন্য একটা ইনসিওরেন্স কোম্পানীকে অধিগ্রহণ করেছে। স্বাভাবিক ভাবেই সেই অধিগ্রীহিত কোম্পানীর কর্মচারীদের মানসিক অবস্থা বা ‘মরাল’ তেমন যুতের নয়। তখন সেই বড় কোম্পানীর কর্তারা ভাবতে বসলেন যে কিছু করে কি এই নতুন কর্মচারীদের মরাল এর উন্নতি করা যায়? ডাকা হল তখনকার দিনের বিখ্যাত অ্যাডভার্টাইজ এবং পাবলিক রিলেশন বিশেষজ্ঞ হার্ভে বল-কে। হার্ভের তখন নিজের ফার্ম ছিল ম্যাসাচুয়েটস-এ। তিনি প্রথমে ওই ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর প্রস্তাব শুনে ভাবলেন, এ আবার কেমন কাজের অনুরোধ! কিন্তু তবুও বললেন, তিনি ভেবে দেখবেন। হার্ভে-কে খুব বেশী দিন এই নিয়ে ভাবতে হয় নি। ইনফ্যাক্ট যেদিন তিনি এই অ্যাসাইনমেন্টের প্রস্তাব পান, সেই দিনই বিকেলে তিনি ড্রয়িং বোর্ডের সামনে ভাবতে শুরু করে একসময় এঁকে ফেললেন একটা হলুদ বৃত্ত, এবং তার ভিতরে দুটো ছোট বৃত্ত এবং একটি অর্ধবৃত্ত!
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালবাবা এবং ঈদ - মোহাম্মদ কাজী মামুন
১৬ জুন ২০২৪ | ৬২ বার পঠিতস্মৃতির সিড়ি দিয়ে নামতে নামতে চলে গেলাম সেই শৈশবের কোন এক ঈদে, আব্বা সংসার চালাতে হিমশিম খাচ্ছিলেন, মামারা ইতোমধ্যে ঈদের শার্ট, প্যান্ট কিনে দিয়েছেন, খালা কিনে দিয়েছেন জুতো, কিন্তু এরপরও আমি কাঁদো কাঁদো, আমার যে অন্য সবার মত দুই সেট জামা চাই, সকাল ও বিকালে বদলে পরার জন্য।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালআমাদের বাবা - Eman Bhasha
১৬ জুন ২০২৪ | ৪৭ বার পঠিতবাবার কথা
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাঅন্ধ ও বধিরের দেশে? - প্রতিভা সরকার
১৬ জুন ২০২৪ | ৪৬৬ বার পঠিতগুরুচন্ডা৯ প্রকাশিত রসিকার ছেলে উপন্যাসে রোহিত ভেমুলার ছায়ায় গড়া কেন্দ্রীয় চরিত্র রোশনের পাশে আছে ফয়জান, স্বনামে নয়, তার নাম ওখানে ফয়জল। তার মৃত্যুর পর মা ছুটে এসেছেন অতদূর থেকে। তাঁর সঙ্গে কেমন ব্যবহার করেছে কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় পুলিশ, তার বর্ণনা আছে। সেই সময় প্রকাশিত বিভিন্ন কাগজের রিপোর্ট ঘেঁটে লেখা। ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে অনেকের ইন্টারভিউ নিয়ে তারপর তিলে তিলে গড়া হয়েছে এই দুর্ভাগা তরুণের চরিত্র। তাকে দাঁড় করানো হয়েছে রোহিত ভেমুলার পাশে। প্রখ্যাত সাহিত্যিক সাধন চট্টোপাধ্যায় এই ২০১৬ এবং ২০২২ কে এক সুতোয় গেঁথে ফেলাকে অন্যায়ের প্রবহমানতা দেখাবার পক্ষে খুবই কার্যকরী হয়েছে বলে ভেবেছেন। আমরা পড়ে দেখতে পারি উপন্যাসের কিছুটা অংশ, যেখানে মায়ের চোখের জল আর প্রবল আকুতি বৃথা হয়ে যাচ্ছে। এমপ্লুরা নামের রাসায়নিক দিয়ে যে নরপশুরা ফয়জানের মৃতদেহ অবিকৃত রাখবার চেষ্টা করেছিল, তাদের নির্লিপ্ততা। রসিকার ছেলে প্রকাশ করে গুরুচন্ডা৯ যে সামাজিক যুদ্ধের সূচনা করেছে, তাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে অমিতাভ চক্রবর্তীদের প্রতিবেদন।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালধ্যান ও স্নায়ুবিজ্ঞান - দ্বিতীয় পর্ব - অরিন
১৬ জুন ২০২৪ | ১১২ বার পঠিতপ্রথম পর্বে আমরা ধ্যান কি ও অনপণসতী নিয়ে লিখেছিলাম । এবারের পর্বে আমরা দেখবো এই ধ্যানের উৎস, মানব মনের প্রবাহ, প্রথম দিকের ব্যবহারিক প্রয়োগ, ধ্যান ও মানব মনের বিচিত্রতা নিয়ে ক্লিনিক্যাল গবেষণা কি বলে ও স্নায়ুবিজ্ঞানের অতি প্রাথমিক কিছু ধ্যান ধারণার অবতারণা ।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালদোলজ্যোৎস্নায় শুশুনিয়ায় - ১৯ - সমরেশ মুখার্জী
১৬ জুন ২০২৪ | ২৫ বার পঠিতআশির দশকে যাদবপুরের কয়েকটি ছাত্রছাত্রী শুশুনিয়া পাহাড়ে গেছে শৈলারোহণ অভ্যাস করতে - সেই ভিত্তিতে এই আখ্যান … চুনি বলে, "জেঠুর পরে কী মনে হয়েছে জানি না। আজ কিন্তু কয়েকবার আমার জেঠুর কাল রাতের কথাগুলো মনে পড়ছিল। দ্যাখ, ও কিন্তু নিজের জায়গায় সৎ। পুরুষের দুর্বলতা, প্রবণতা যাই হোক, ছেলে হিসেবে ও যেভাবে ভেবেছে তা ও পরিস্কারভাবে বলেছে। সেটাই সামগ্ৰিকভাবে পুরুষ জতের বৈশিষ্ট্য কিনা তা নিয়ে বিতর্ক হতে পারে। কিন্তু মেয়ে হিসেবে আমাদের তো ওর কথাগুলো ফ্যালনা মনে হয়নি। কিন্তু মেয়েদের ওপর অত্যাচারের জন্য পুরুষের দিকে আঙুল তোলা ছাড়া ঈশু কি মেয়েদের আচরণের ব্যাপারে কিছু বলেছে? তাহলে পুরুষের দিকে তোলা অভিযোগের তীরগুলো কিছুটা ভোঁতা হয়ে যায়। তাই না?"
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালএমনি একটা সিরিজ থেকে, কবিতার টইটা কৈ? এখানেই থাক যত্তসব - একক
১৬ জুন ২০২৪ | ১২৩ বার পঠিতযা হজম হয়েনা উহা, কবিতা, ন্যুনপক্ষে কবিতার প্রলাপপ্রয়াসী। নীলচে ফ্রিজের বই, স্টেডি নারী , স্বতঃসিদ্ধ কাচার মেশিন- সকলি সাক্সেস ভেল ; শুধু এই বিষ্ঠা এই অগম্য পুরীষ, চেম্বার উপচে পড়চে নৃতছন্দে নষ্টা উপমায়, একে নাও,
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালনন্দীগ্রাম ফন্দিগ্রাম - Naresh Jana
১৬ জুন ২০২৪ | ২৭১ বার পঠিতমাও ফাও, বাপ ব্যাটা আর পিসি। কিসি জমিতে হিসি করে ভেড়ি হচ্ছে। নো ভোট্টু ঘাসফুল দিয়ে জাপানি ইকেবানা সাজাচ্ছে।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালWriter's Block এলে কী করেন? - শুভংকর
১৫ জুন ২০২৪ | ১৪৪ বার পঠিতWriter's Block
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালপশ্চিমবঙ্গে সরকারি স্কুল শিক্ষার মান কী কমছে? - Anirban M
১৫ জুন ২০২৪ | ২৮৮ বার পঠিতপশ্চিমবঙ্গে সরকারি স্কুল শিক্ষার মান কী কমছে? বিশেষতঃ রাজ্যে ক্ষমতা পরিবর্তনের পরে কী রাজ্যের সরকারি স্কুল শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে? এই প্রশ্নগুলির উত্তর বোঝার চেষ্টা করব Annual Status of Education Report এর ভিত্তিতে।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালসিন্দবাদের গল্প ছড়ানো ছাদে - সুকান্ত ঘোষ
১৫ জুন ২০২৪ | ৫২ বার পঠিতও বাড়ির দুয়ার থেকে কেউ বলেছিল যেতেই কি হবে আজ? থেকেই যদি যায় বৈঠকখানার ঘরে? আজ রাতে চাঁদ উঠবেনা, চিনতেও চাইবে না কেউ সেই অস্ফুট আলোয় এলোমেলো চুলের ফাঁকে লাল রঙ অসময়ের বর্ষা বাতি নিভিয়ে দিয়েছে অনেকক্ষণ
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজামহারাজ ছনেন্দ্রনাথ ও বিদেশি চকলেটের বাক্স - রমিত চট্টোপাধ্যায়
১৫ জুন ২০২৪ | ৩১৬ বার পঠিতআজকে সকালে তেতলার পিসিমার কাছে যে চিঠিটা এল, দাদা মানে পিসিমার ছেলে অনেকক্ষণ ধরে পিসিমাকে পড়ে পড়ে শোনাচ্ছে। ছেনু গিয়ে দু'বার দরজার সামনে থেকে ঘুরেও এল, কত লম্বা চিঠি রে বাবা! শেষে আর থাকতে না পেরে ছেনু গিয়ে পিসিমাকে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করেই ফেলল, কার চিঠি গো? দেখা গেল অদ্ভুত ব্যাপার, পিসিমা হাসছে, অথচ চোখের কোণে জল, পিসিমা হেসে বলল, কে আসছে জানিস? কান্টু আসছে রে কান্টু, তোর কান্টু দাদা। এদ্দিন পর ও আসছে, শুনে বিশ্বাসই করতে পারছি না, তাই তো বারবার করে শুনছি। ছেনু ছোট্ট থেকে পিসিমার কাছে কান্টুদার অনেক গল্প শুনেছে, কিন্তু কোনোদিন কান্টুদাকে চোখে দেখেনি আজ পর্যন্ত। অবশ্য দেখবেই বা কি করে, ছেনুর জন্মের আগেই তো পিসিমার বড় ছেলে কান্টুদা সেই সাত সমুদ্দুর তেরো নদী পার করে কি একটা দেশ আছে, কানাডা না কি নাম, সেইখানে চলে গিয়েছিল। সেই থেকে সেখানেই থাকে আর মাঝে মধ্যে চিঠি লিখে খবরাখবর জানায়। শুরুর দিকে বাংলায় লিখত বটে কিন্তু পরে কি জানি কেন শুধু ইংরেজিতেই চিঠি পাঠায়, তাই অন্যরা পিসিমাকে তর্জমা করে পড়ে পড়ে শোনায় কি লিখেছে।
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাবিপ্লবের আগুন - পর্ব নয় - কিশোর ঘোষাল
১৫ জুন ২০২৪ | ৮৯ বার পঠিততোমার মনে আছে, কবিরাজদাদা ওর শরীরের লক্ষণ দেখে বলেছিলেন, ভল্লা সাধারণ এলেবেলে ছেলে নয়। যথেষ্ট শক্তিশালী যোদ্ধা। আরও বলেছিলেন, ওই চরম অসুস্থ অবস্থায় ওর এখানে আসাটা হয়তো আকস্মিক নয়। হয়তো গোপন কোন উদ্দেশ্য আছে। আজকে সকলের সামনে কবিরাজদাদা সে প্রসঙ্গ তোলেননি। কিন্তু আমারও এখন মনে হচ্ছে কবিরাজদাদার কথাই ঠিক”।
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাফৈজান আহমেদ আত্মহত্যা করেন নি - অমিতাভ চক্রবর্ত্তী
১৫ জুন ২০২৪ | ৫৭১ বার পঠিতনির্মম হত্যাকান্ড! খুন হয়েছিলেন আই আই টি খড়গপুরের মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র ফৈজান আহমেদ? কি ভাবে? গত ২১শে মে ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ ডক্টর অজয় গুপ্তা কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর বেঞ্চকে জানান যে ফৈজানকে মাথার পিছনে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হয়েছিল, ঘাড়ের জায়গায় ছুরির আঘাত করা হয়েছিল এবং তার পর পিছন থেকে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে ঘাড়ে গুলি করা হয়েছিল। (১৩-ই জুনের ই-নিউজরুম ইন্ডিয়ার প্রকাশিত সংবাদ)। এই রিপোর্ট মৃতদেহের দ্বিতীর ময়নাতদন্তের ফল। কেন দু’বার ময়নাতদন্ত? কারণ, প্রথম ময়নাতদন্তে এতগুলি চিহ্নর কোন কিছু নজরে আসে নি আর মৃত্যুর কারণ সাব্যস্ত হয়েছিল আত্মহত্যা। নিজের হস্টেল ঘর থেকে ২৩ বছরের ছেলেটির অর্ধ-গলিত মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল। আই আই টি কর্তৃপক্ষ এবং পুলিশের বক্তব্য অনুসারে তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন। ফৈজানের মৃত্যুর খবর পেয়ে তার পরিবার খড়গপুরে পৌঁছে তার মৃতদেহ দেখে এই মৃত্যুকে আত্মহত্যা বলে মানতে অস্বীকার করেন। তারা বলেন ফৈজান র্যাগিংয়ের শিকার এবং তিনি খুন হয়েছেন। ফৈজানের মা-বাবা কলকাতা হাইকোর্টে পিটিশন দাখিল করেন। পোস্ট-মর্টেম রিপোর্টে অসঙ্গতি নজরে আসায় হাইকোর্ট মৃতদেহ কবর থেকে তুলে নিয়ে এসে দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্ত করার আদেশ দেয়।
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাজাগছে সেঙ্গল! অরণ্য আর আদিবাসী উৎপাটনের হুংকার - নরেশ জানা
১৫ জুন ২০২৪ | ৪৭৩ বার পঠিত২০১৮-র ডিসেম্বরে পার্লামেন্টে সরকার জানায় যে, ২০১৫ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে মোট ২০,৩১৪.১২ হেক্টর বনভূমি কর্পোরেট সংস্থার হাতে খনিজ পদার্থ উত্তোলনের জন্য তুলে দেওয়া হয়েছে। যদিও আদিবাসীদের আন্দোলন, গ্রামসভা গুলির আপত্তি ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে কর্পোরেট সংস্থাগুলোর পক্ষে কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ায় কিছু সমস্যা হচ্ছিল, বিশেষ ছত্তিশগড়ের গভীর অরণ্য বেষ্টিত আদিবাসী জনজাতি নির্ভর এলাকাগুলিতে। ২০২৩ সালের নভেম্বরে ছত্তিশগড়ে বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসকে পরাজিত করে সরকার গঠন করে বিজেপি। এখানেও কায়দা করে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী করা হয় বিজেপির আদিবাসী নেতা বিষ্ণু দেও সাই কে। ২০২৪ ডিসেম্বর মাসে শপথ নেন তিনি আর জানুয়ারি থেকেই গৌতম আদানির কোম্পানি শুরু করেছে নির্বিচার অরণ্য নিধন।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালবৈঠকি আড্ডায় ১৮ - হীরেন সিংহরায়
১৫ জুন ২০২৪ | ২৩৮ বার পঠিতগাড়ির ড্যাশ বোর্ডের স্পিডোমিটার দেখলে জানা যায় তাঁর উচ্চতম গতি বেগ ঘণ্টায় দুশো কিলোমিটার । এই সব মূল্যবান তথ্য জানিয়ে বিক্রেতারা মহার্ঘ্য গাড়ি বিক্রি করেন । গাড়ির শো রুম থেকে বেরুলেই চোখে পড়ে নোটিস - শহরের ভেতরে গাড়ির গতির উচ্চসীমা ঘণ্টায় বিশ মাইল, একটু দূরে গেলে তিরিশ। মোটরওয়েতে ৭০ মাইল ( ১১২ কিমি ) গতি অনুমোদিত । সেখানে কদিন যাই ? যেখানে আমার নিত্যিদিনের ঘোরাঘুরি - হাটে বাজারে , বন্ধু সন্দর্শনে সেখানে আমার গাড়ির টিকিটি বাঁধা আছে তিরিশ বা বড়জোর পঞ্চাশ মাইল বেগে । প্রয়াত ভাস্করদার ( ভাস্কর দত্ত , সুনীলদার অভিন্ন হৃদয় বন্ধু) পুত্র অর্ণবের বাড়ি থেকে কিছু সঞ্চিত বই সংগ্রহের জন্য উত্তর লন্ডনের স্টোক নিউইংটন গেলাম গত রবিবার - এককালের সেই বিখ্যাত ওয়েস্টওয়ে আকীর্ণ হয়ে আছে অজস্র ক্যামেরায়, ওয়েম্বলি, হ্যামারস্মিথ থেকে কিংস ক্রস ছাড়িয়ে গাড়ি চলে ধীরে মন্দ গতিতে, আইন বাঁচিয়ে ।
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাকাদামাটির হাফলাইফ - ইট পাথরের জীবন - ইমানুল হক
১৫ জুন ২০২৪ | ১২৩ বার পঠিতমায়ের সঙ্গে ছেলের প্রবল মতাদর্শগত অমিল। অথচ এই অবিবাহিত ছেলেকে ঘিরেই মায়ের গোপন আবেগ। ভালোবাসা। ছেলে সূর্যকুমার যখন সংসার ভেঙ্গে ভাগ হয়ে যাচ্ছে, মানতে না পেরে এবং অন্যান্য কারণে আত্মহত্যা করে। আমাদের ছোটবেলায় অভাবের জ্বালায় সংসার চালাতে না পেরে পুরুষ বা নারীর আত্মহত্যার চেষ্টা দেখেছি। তবে এক 'মুসলিম' তরুণীর প্রেমে এক 'হিন্দু' তরুণের আত্মহত্যা গ্রামে খুব আলোড়ন তোলে।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালদিলদার নগর ৪ - Aditi Dasgupta
১৪ জুন ২০২৪ | ১৭২ বার পঠিতঘটমান বর্তমান ঘটেনাতো পিছনের কথামুখ ভুলি। দিলদরিয়াতে নেমে একে একে খুলে যায় -- এ ‘আমির’ আবরণ গুলি।।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালকিষেণজি মৃত্যু রহস্য - পর্ব ১৩ - বিতনু চট্টোপাধ্যায়
১৪ জুন ২০২৪ | ১৬৩ বার পঠিতমিনিট খানেক বাদে এসপি ফোন ছেড়ে বললেন, ‘‘কিছু হয়নি তেমন। ইলেকট্রিকের তার ছিঁড়ে পড়েছে কনভয়ে পুলিশের গাড়ির ওপর। তাতেই টাল সামলাতে না পেরে পুলিশের গাড়ি রাস্তার ধারে পড়ে গিয়েছে।’’ এসপির কথায় আশ্বস্ত হলেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফোন ছেড়ে প্রভীণ কুমার জানালেন, ‘‘স্যার, ব্লাস্ট হয়েছে। ব্লাস্টে ইলেকট্রিক তার ছিঁড়ে মাটিতে পড়েছে। জোরে আওয়াজ হয়েছে, বড় ব্লাস্ট ছাড়া তা হতে পারে না।’’
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজানিট কেলেঙ্কারি - পর্দা ফাঁস - ভিডিওগুরু
১৪ জুন ২০২৪ | ৪২৩ বার পঠিতনিট কেলেঙ্কারি নিয়ে নিয়ে বাংলা মিডিয়া এখনও মোটামুটি চুপচাপ, যেটুকু না বললে নয়, সেইটুকু বলছে। যদিও এরকম হবার সম্ভাবনা আছে, যে, নিটই স্বাধীন ভারতবর্ষের বৃহত্তম কেলেঙ্কারি। হ্যাঁ, আদালতের রায়ের পরেও ব্যাপারটা বদলায় না। কিন্তু মূলধারার মিডিয়ার হাতে ছেড়ে দেব বলে তো আমরা কাজ করছিনা। এই ভিডিওটা দেখুন, বিশদে পুরোটা বলা আছে।
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাপ্রথম ব্ল্যাক হোল - সহস্রলোচন শর্মা
১৩ জুন ২০২৪ | ১৬৮ বার পঠিতব্ল্যাক হোল?! ননসেন্স! বাস্তব জগতে ব্ল্যাক হোল বলে কোনও কিছুর অস্তিত্বই নেই। অস্তিত্ব থাকতে পারে না। এটা নেহাতই গণিতের একটা ফসল মাত্র। ‘ব্ল্যাক হোল’ হলো তাত্ত্বিক পদার্থবিদদের উর্বর মস্তিষ্ক প্রসূত এক কল্পনা বিলাস। এই কল্পনার না আছে কোনও বাস্তব ভিত্তি না আছে কোনও বাস্তব প্রমাণ। এমনটাই মনে করতেন সেই সময়ের অধিকাংশ বিজ্ঞানীরা। কেউ কেউ যদিও ব্ল্যাক হোলের অস্তিত্বের উপর ভরসা রাখতেন। তবে সেই সময়ে, ঈশ্বরে বিশ্বাস করার মতোই ব্ল্যাক হোলে বিশ্বাস করাও ছিল প্রমাণহীন একটা ধারণা মাত্র।
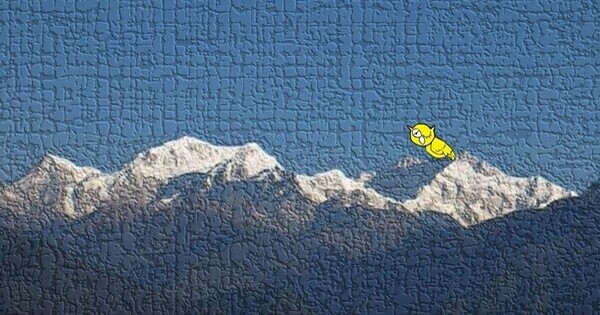 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাভ্রান্তিপর্বত শান্তিতীর্থ - নন্দিনী সেনগুপ্ত
১৩ জুন ২০২৪ | ১৬৪ বার পঠিতচলতি বছরে মে মাসের প্রথম সপ্তাহে উত্তরাখণ্ডে পাঁচ জন মানুষের মৃত্যু ঘটেছে দাবানলে। প্রশ্ন উঠতে পারে যে দাবানলে মানুষ মরল কী ভাবে? কারণ দাবানল অরণ্যে হয়। তাহলে কি দাবানল এত বিধ্বংসী আকার ধারণ করেছে যে সেই আগুন ছড়িয়ে পড়েছে অরণ্যের পাশের জনপদে? এক্ষেত্রে সম্ভাব্য কারণ বলা হচ্ছে মানুষ দাবানল নেভাবার চেষ্টা করতে গিয়ে ঘটেছে এই ঘটনা। পাহাড়ে আদিবাসীদের একটা বড় অংশের মানুষের কাছে বৃক্ষ এবং অরণ্যের মহিমা দেবতার মত। পরিবেশবিজ্ঞান বইয়ের পাতা উল্টে শেখে না তারা। জন্ম থেকেই মানুষ প্রকৃতির হাত ধরে বাঁচে সেখানে, ফলে নাগরিক সভ্যতার বৃত্তের বাইরের মানুষ বৃক্ষদেবতা তথা অরণ্যকে বাঁচাবার চেষ্টা করবে, এমন ঘটনা নতুন নয়।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালতোমার বাস কোথা যে... - ৬ - Nirmalya Nag
১৩ জুন ২০২৪ | ৩১১ বার পঠিতফোনে কথা বন্ধ করল ইন্দ্রনীল, জামার পকেটে মোবাইল রেখে দুজনের দিকে একবার তাকাল। তারপর খামটা এগিয়ে দিল বিনীতার দিকে, সে ওটা হাতে নিল। ইন্দ্রনীল দেখল অরুণাভর বই বুকের ওপর খোলা, চোখ তারই দিকে। “সার্জারি ভালই হয়েছে। কিন্তু কন্ডিশন ভাল নয়। টিউমারটা ম্যালিগন্যান্ট,” কথা বলতে বলতেই ডাক্তার দেখল অরুণাভর চোখ বইয়ের দিকে ঘুরল। “আমি অকারণ আশা দিতে চাই না। মেটাস্টেসিস শুরু হয়েছে, মানে ছড়িয়ে গেছে রোগ, স্টেজ ফোর।” বিনীতা বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল ইন্দ্রনীলের দিকে, তারপর দেখল তার স্বামীর দিকে। তার চোখ বইয়ের পাতায়, তবে মন কোথায় বলা কঠিন।
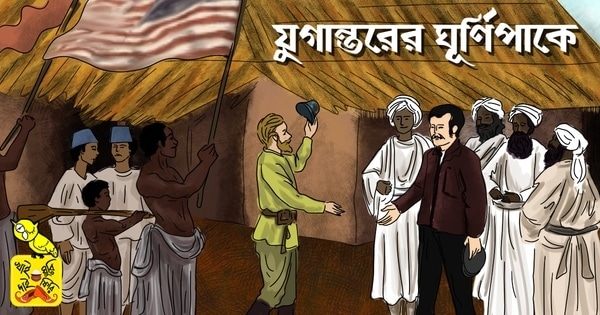 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাডেভিড লিভিংস্টোনের খোঁজে-১৪২ - হেনরি মর্টন স্ট্যানলে
১৩ জুন ২০২৪ | ৫৫ বার পঠিতআমাদের শিবির থেকে, আমেরিকান কনসালের কাছে চিঠি দিয়ে তিনজনকে জাঞ্জিবারে পাঠিয়েছিলাম, সেই সঙ্গে 'হেরাল্ড'-এর কাছে টেলিগ্রাফ পাঠানোর জন্যও। রাজদূতকে অনুরোধ করেছিলাম যে তিনি যেন একটা-দুটো ছোট বাক্স ভরে কিছুমিছু বিলাসদ্রব্য দিয়ে লোকদের ফেরত পাঠান যা ক্ষুধার্ত, জীর্ণ, ছ্যাতলাধরা মানুষজন তারিফ কুড়াবে। বার্তাবাহকদের বৃষ্টি- অনাবৃষ্টি, নদী- বন্যা কোনো কিছুর জন্যই থামতে বারণ করা হয়েছিল - যাতে তারা তাড়াহুড়ো করল না আর তারা উপকূলে পৌঁছানোর আগেই আমরা তাদের ধরে ফেললাম এমন ঘটনা না ঘটে। প্রবল উৎসাহে "ইনশাআল্লাহ, বানা" বলে তারা রওনা দিল।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালসিঙ্গুরের পরের স্টেশন - সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায়
১৩ জুন ২০২৪ | ১০৮২ বার পঠিতসিঙ্গুরের পরের স্টেশন কামারকুন্ডুতে, প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান শুনলাম, এক হকারকে আরপিএফ গুঁতো মেরে ট্রেনে থেকে ফেলে দিয়ে মেরে ফেলেছে বলে অভিযোগ। কেন্দ্রীয় বাহিনী। পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত এলাকায়, কিছুদিন আগেই বিএসএফ একজনকে গুলি করে মেরে ফেলেছিল বলে অভিযোগ। কেন্দ্রীয় বাহিনী। তাদের দাপাদাপি সীমান্ত ছাড়িয়ে অনেক দূর পর্যন্ত। কান পাতলেই অভিযোগ শুনতে পাওয়া যায়। তাদের দাপাদাপি রেলে। কান পাতলেই শুনতে পাবেন অত্যাচারের অভিযোগ। বাঙালিদের তুলে হিন্দুস্তানিদের বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে হকার হিসেবে, স্টেশনের স্থায়ী স্টলগুলোতে হিন্দিভাষীদের অস্বাভাবিক বাড়বৃদ্ধি।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালধ্যান ও স্নায়ুবিজ্ঞান - অরিন
১২ জুন ২০২৪ | ১৭৮১ বার পঠিতজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মনোনিবেশ এবং ধ্যান ব্যাপারটির অপরিসীম তাৎপর্য। ধ্যান ব্যাপারটিকে ধর্ম, রীতিনীতি বা মনোবিজ্ঞান থেকে একটু সরিয়ে দেখা যাক। একটা প্রশ্ন ওঠা খুবই স্বাভাবিক: যে ধ্যান করলে মনের "গভীরে" হয় কি? যদি সত্যি কিছু হয়, তাকে জানা যাবে কোন উপায়ে? কোনটা বিজ্ঞান আর কোনটা নয়? এই প্রশ্নগুলোকে কেন্দ্র করে আমাদের মস্তিষ্ক, এবং চেতনার একটা আকর্ষণীয় দিক নিয়ে আলোচনার ব্যাপার রয়েছে। বিশেষ করে, ধ্যান বিষয়টিকে কেন্দ্র করে স্নায়ুবিজ্ঞান (নাকি স্নায়ুশাস্ত্র) ও কম্পিউটার বিজ্ঞানের মেলবন্ধনে চিন্তাভাবনার একটি নতুন দিক উন্মোচিত হচ্ছে।
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাখাদ্য এবং খাদ্য ফসলের দূষণ একটি নীরব ঘাতক - সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপ ও সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ন সমাধান - শ্যামল অধিকারী
১২ জুন ২০২৪ | ৩৩৮ বার পঠিতFSSAI (ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া) এর চরম ব্যর্থতা। খাদ্যদ্রব্যের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে এবং রাসায়নিক পেস্টিসাইড নিয়ন্ত্রণ করতে FSSAI সম্পূর্ণ ব্যর্থ। দায়ের করা একটি পিটিশনে বলা হয়েছে যে কীটনাশক যুক্ত খাবারের ব্যবহার সারাদেশে ক্যান্সার রোগের প্রধান কারণ হয়ে উঠেছে এবং তাতে মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে। কীটনাশক এবং ক্যান্সারের মধ্যে একটি সরাসরি বৈজ্ঞানিক সম্পর্ক রয়েছে। ফলে কীটনাশক যুক্ত খাবার, তার ব্যবহার, অতিব্যবহার এক বিরাট চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আবেদনকারী সারা দেশ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন যা দেখায় যে কীটনাশকের কারণে মৃত্যুর সংখ্যা বেশি হচ্ছে। সিনিয়র আইনজীবী অনিথা শেনয়, আবেদনকারী অ্যাডভোকেট আকাশ বশিষ্ঠের পক্ষে উপস্থিত হয়ে সুপ্রিম কোর্টকে জানালেন। পাশাপাশি পিটিশনে ক্যালসিয়াম কার্বাইড এর মতো রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে ফল কৃত্রিমভাবে পাকানো, আপেলের মত ফলগুলির রং বা আবরণ প্যারাফিন, শেলাক এবং পলিথিনের মত উপাদান দিয়ে তৈরি মোম দিয়ে পলিশিংয়ের বিষয়টিও উল্লেখ করা হয়। এছাড়া ডাল এবং খাদ্যশস্যে কৃত্রিম রং ব্যবহারের কথাও উল্লেখ করা হয়। ভারতের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বে সুপ্রিম কোর্টের এক বেঞ্চ 17 মে, 2024 পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক, কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা ও মান অথরিটি অফ ইন্ডিয়াকে (FSSAI) নোটিশ জারি করেছে এবং তাদের প্রতিক্রিয়া চেয়েছে।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালমোদি কি আদৌ বারানসীতে জিতেছেন? - সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায়
১২ জুন ২০২৪ | ৩২০ বার পঠিতমোদি কি আদৌ বারানসীতে জিতেছেন? ফলাফল বেরিয়ে যাবার পর এই প্রশ্ন কেন? কারণ, অন্য কেউ না, বিজেপির নেতারাই প্রশ্নটা তুলছেন। গোপন কিছু না। আস্ত সাক্ষাৎকার বেরিয়েছে। কিন্তু খুব সম্ভবত আপনি দেখেননি, কারণ মিডিয়া দেখায়নি। বা যৎসামান্য দেখিয়েছে। ওদিকে ব্যাপারটা কিন্তু বিস্ফোরক। তাই আমরাই ভিডিও সমেত জিনিসটা সামনে নিয়ে এলাম। আমাদের চ্যানেল এখনও পুরোদস্তুর তৈরি না। কিন্তু এইসব জিনিস এলে এখনও সঞ্চালকরা তৈরি না বলে তো থেমে থাকা যায়না। তাই করে ফেলা হল। কেন করে ফেলতে হল, সে দেখলেই বুঝতে পারবেন।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালদোলজ্যোৎস্নায় শুশুনিয়ায় - ১৮ - সমরেশ মুখার্জী
১২ জুন ২০২৪ | ৬৩ বার পঠিতআশির দশকে যাদবপুরের কয়েকটি ছাত্রছাত্রী শুশুনিয়া পাহাড়ে গেছে শৈলারোহণ অভ্যাস করতে - সেই ভিত্তিতে এই আখ্যান … যতই মুড অফ থাকুক, কেউ লুজ বল দিলে ছক্কা মারার জন্য সুমনের মন নিশপিশ করে। ভাবলেশহীন মুখে বলে, "তোর সাথে একা গল্প করতে আমার ভয় করে।" কোমরে দু হাত দিয়ে তুলি লড়াকু ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে বলে, "ভয় করে! কেন? আমি কী কামড়ে দেবো তোকে?"
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালচললুম ঈর্ষাহীন দেবীর গৃহে (সমাপ্ত) - সমরেশ মুখার্জী
১১ জুন ২০২৪ | ২৯০ বার পঠিত"একা বেড়ানোর আনন্দে" - এই সিরিজে আসবে ভারতের কিছু জায়গায় একাকী ভ্রমণের অভিজ্ঞতা। এটি পর্ব - ২৮ … দুবার একই ভুল করে একটি জনশ্রুতির মর্মার্থ উপলব্ধি করেছি কাঁপতে কাঁপতে - ছাগল দিয়ে লাঙ্গল দেওয়া গেলে চাষা বলদ কিনতো না। সেবার উত্তরাখণ্ড ভ্রমণে পঞ্চকেদারের দুটি কেদারে গেছিলাম। একাকী যোশিমঠ থেকে কল্পেশ্বর। ছ জনের দলে তুঙ্গনাথ। দলটি হয়েছিল গুপ্তকাশীতে আলাপ পাঁচটি উত্তরপ্রদেশের তরুণের সাথে। তুঙ্গনাথ, দেওরিয়া তালে দুটি রাত কাটিয়ে উখিমঠ থেকে ওরা হরিদ্বার চলে যেতে আবার আমি একা
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাহাসপাতালের ডায়েরি - পারমিতা চৌধুরি
১০ জুন ২০২৪ | ৬০৮ বার পঠিতএ বছর চৈত্রের শুরু থেকেই ঝলসে দেওয়া শুকনো গরম। সেই গরমে sskm এর এক একটা লাইনে তিন ঘন্টা দাঁড়িয়ে নারী পুরুষ। মেয়েরা এখানে সংখ্যাগুরু। সংসারের যাবতীয় কাজ ভোর রাতে উঠে সামলে তারা চলে আসে। কখনো নিজের জন্য, কখনো সন্তানের জন্য। এমনকি এমন মেয়ের দেখা পেয়েছি যে sskm চেনে হাতের তালুর মত আর তার হাত ধরে প্রথমবারের জন্য ডাক্তার দেখাতে এসেছে তার স্বামী। মেয়েরা না কি রাস্তা পেরোতে পারে না
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালকাটাকুটি - সমরেশ মুখার্জী
১০ জুন ২০২৪ | ১০৯ বার পঠিতএটা আজই আমার পাতায় পোষ্টিত “টুনটুন মুনটুন”- লেখার প্রলম্বিত পুনশ্চঃ
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালটুনটুন মুনটুন - সমরেশ মুখার্জী
১০ জুন ২০২৪ | ২২১ বার পঠিতকঠোরভাবে প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য - দেশব্যাপী পঞ্চবার্ষিকী যাত্রাপালা সদ্যসমাপ্ত হয়েছে। বিগত কয়েক হপ্তা ধরে তাই নিয়ে এন্তার কূটকচা৯ দেখেশুনে মনপ্রাণ ভারাক্রান্ত। কিছু মাস বাদে ঐ রঙ্গপালাই চলবে আরো কিছু প্রদেশে আঞ্চলিক পর্যায়ে। তার মাঝে একটু হালকা হতে লিখলুম এই চিরন্তন লীলাপ্রসঙ্গ … তবে তরল আঙ্গিকে
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাদুয়ারসিনি - নরেশ জানা
০৯ জুন ২০২৪ | ২৪৮ বার পঠিতরাস্তায় নেমেই ঘড়ির কাঁটায় নজর দিয়ে দেখে নিয়েছি বেলা তখন দশটা বেজে পনেরো। ঝাড়খন্ড আর বাংলার আকাশ থেকে তখনও ঘূর্ণাবর্তের ছায়া কাটেনি বটে কিন্তু এখন এই মুহূর্তে সোনার মত রোদ গলে পড়ছে। গুগল ট্র্যাকার দেখে ঝিলমিল আর রাগিণী আমাকে জানালো আমাদের হাঁটতে হবে এক কিলোমিটার পথ। মৃত্যুঞ্জয় গাড়িটা নিয়ে এগিয়ে গেছে, গীয়ার নিউট্রাল করে শব্দহীন গাড়ি নেমে গেছে সুন্দরী দুয়ারসিনির পথে। আমাদের সাথেও রয়েছে চার সুন্দরী। রুশতি আজ জিন্স্ পরেছেন। নীল ফেডেড জিন্সের ওপর লাল আর কালো স্ট্রাইপ দেওয়া সাদা শার্ট। মেয়ে রাগিণী আজ পুরোপুরি কালো পোশাকের আশ্রয় নিয়েছে। স্লিভলেস ঝালর দেওয়া কালো টপ আর পালাজো। রিয়ানের আজ কমলা আশ্রয়। কলার দেওয়া হাঁটু ছাড়ানো কুর্তি আড়াল করেছে কালো চোস্তা পাজামাকে। ঝিলমিল একটা মেরুন পাজামার ওপর কালো টি শার্ট চড়িয়েছে।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালদোলজ্যোৎস্নায় শুশুনিয়ায় - ১৭ - সমরেশ মুখার্জী
০৯ জুন ২০২৪ | ৭৫ বার পঠিতআশির দশকে যাদবপুরের কয়েকটি ছাত্রছাত্রী শুশুনিয়া পাহাড়ে গেছে শৈলারোহণ অভ্যাস করতে - সেই ভিত্তিতে এই আখ্যান …একটা অবুঝ অভিমান দলা পাকিয়ে উঠছে সুমনের মনে। মলয়দা রেশনিং করে খেতে বলা সত্ত্বেও ওরা কিছুটা জল বাঁচিয়ে রাখতে পারলো না ওদের জন্য? এই ফেলো ফিলিংস নিয়ে এরা পাহাড়ে যাবে?
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাএমনি এমনি মারি - রমিত চট্টোপাধ্যায়
০৮ জুন ২০২৪ | ৫৭১ বার পঠিত বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাস্লোভাকিয়া ৫ - হীরেন সিংহরায়
০৮ জুন ২০২৪ | ৪৯৬ বার পঠিত হরিদাস পাল
হরিদাস পালচললুম ঈর্ষাহীন দেবীর গৃহে - ২ - সমরেশ মুখার্জী
০৮ জুন ২০২৪ | ১৭৬ বার পঠিত"একা বেড়ানোর আনন্দে" - এই সিরিজে আসবে ভারতের কিছু জায়গায় একাকী ভ্রমণের অভিজ্ঞতা। এটি পর্ব - ২৭ … পরিচিত সঙ্গীর সাথে হপ্তা দুয়েক অবধি ভ্রমণ ঠিক আছে। তার বেশী হলে নানা কারণে ছানা কাটতে শুরু করে। কিন্তু দু মাসের একাকী ভ্রমণেও কখনো সঙ্গীহীনতার চাপ অনুভব করিনি। সেলফ ড্রাইভ করে বেড়াতে গেলে বাস্তবিক কারণে সাথে একজন থাকলে সুবিধা হয়। কারণ পথে গাড়ি খারাপ হতেই পারে। জনবাহনে গেলে সে প্রয়োজন নেই। একাকী ভ্রমণে সঙ্গীর অভাব বোধ না করলেও চলার পথে স্থানীয় মানুষের সাথে গল্পগুজব করতে ভালোই লাগে। যাদের সাথে আর কখনো দেখা হবেনা তাদের সাথে ক্ষণিকের আলাপ স্মৃতিতে রয়ে যায় বহুদিন
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাবিপ্লবের আগুন - পর্ব আট - কিশোর ঘোষাল
০৮ জুন ২০২৪ | ১৪৩ বার পঠিতপ্রথম দিন আলাপের সময়েই এই দলটি তার কাছে বিদ্রোহের মন্ত্র জানতে চেয়েছিল। সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে একত্রে লড়ে যাওয়ার শপথ নিয়েছিল। বলেছিল ভল্লাদা তুমি একা, তাই ওরা তোমাকে এভাবে চূড়ান্ত হেনস্থা করতে পেরেছে। তোমার ওপর ঘটে যাওয়া এই অপমানের শোধ তুলব আমরা সবাই মিলে। ভল্লা মনে মনে হেসেছিল। একটু বিদ্রূপের সুরে গম্ভীর মুখে ভল্লা বলেছিল, “খাওয়া, ঘুমোনো আর হাগতে-পাদতে-মুততে যাওয়া ছাড়া আর কী পারিস? ছুটতে পারিস? লাফাতে পারিস? গাছে উঠতে পারিস? সাঁতার কাটতে পারিস? অস্ত্র চালাতে পারিস কিনা জানতে চাইলাম না। জানি, ও জিনিষ তোরা কোনদিন হাতেও ধরিসনি”।
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাপরিযায়ী শ্রমিক, মহিলা ভোটার আর ২০২৪ নির্বাচনের কিছু গণিত - সুদীপ্ত পাল
০৮ জুন ২০২৪ | ৩৩৭ বার পঠিতমঙ্গলসূত্র, মুসলিম, মাটন, মাচ্ছি, মোষ, মুজরা- এসবের মাঝে যে দুটো ম-এর কাহিনী চাপা পড়ে গেছে সেটা হল মহিলা ভোটার আর মাইগ্রেন্ট লেবারার। ২০২৪ এর লোকসভা নির্বাচনের প্রথম দুই দফায় যে বিষয়টা নজর কেড়েছিল সেটা ছিল ভোট শতাংশ কমে যাওয়া। নির্বাচনের শেষের দিকে যেটা নজর কেড়েছে সেটা হল পুরুষদের চেয়ে নারীদের বেশিমাত্রায় অংশগ্রহণ। নারীদের মধ্যে অতিরিক্ত ভোটদানের হার বিশেষভাবে দেখা গেছে বিহার, পূর্ব উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলায় এবং ঝাড়খণ্ডে। সবচেয়ে লক্ষণীয় হল বিহার। বিহারে প্রথম দফায় নারীদের ভোট শতাংশ পুরুষের চেয়ে কম ছিল। দ্বিতীয় দফা থেকে বাড়তে শুরু করে। বিহারে যেটা কমেছে সেটা হল পুরুষদের ভোটদানের হার- এটা ৫৫.১% থেকে ৫৩.৩% এ নেমে এসেছে। মহিলাদের ভোটদানের হার ৫৯.৪% যা ২০১৯এর প্রায় সমান।
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাকাদামাটির হাফলাইফ - ইট পাথরের জীবন - ইমানুল হক
০৮ জুন ২০২৪ | ২৩২ বার পঠিতহিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ মুরগি পালন করতেন না। তাঁদের ঘরের মেয়েরা হাঁস পালন করতেন। কোনও হিন্দু বাড়িতেই মুরগি ঘরে রান্না করা যেত না। ফিস্টিতে খেতে হতো। মুরগিকে বলা হতো রামপাখি। মুরগির ডিমকে রামফল। জ্বর সর্দি হলে শরীর দুর্বল হলে প্রেসার লো হলে গ্রামের ডাক্তার মুরগির হাফ বয়েল ডিম খেতে নিদান দিতেন। তখন মুসলিম বাড়িতে গিয়ে মুরগির ডিম কিনে আনতে যেতো। এখন তো মুরগির মাংস জলভাত পোল্ট্রির কল্যাণে। এই পোল্ট্রি আমাদের গ্রামে আসে বামফ্রন্টের বেকার ভাতা দেওয়ার কল্যাণে। বেকার ভাতা পেতেন তিনজন। তিনজনই কংগ্রেসি। এঁরা ম্যাট্রিক পাস করে কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রে নাম লিখিয়েছিলেন। নাসির চাচা ও সালাম চাচা ছিলেন উদ্যোগী মানুষ। দুজনেই আমার খুব পছন্দের মানুষ। তাঁদের রাজনীতি আমাদের পরিবারের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপনে কোনও বাধা হয়নি। বামপন্থী রাজনীতির কারণে ২০০৯ থেকে আমাদের পরিবারকে বয়কট করা হলেও সালাম চাচা, ধনা চাচা ও মাদু চাচা নিয়মিত যোগাযোগ রেখেছেন। এসেছেন। আর এসেছেন ব্রাহ্মণ সন্তান পীরে কাকা। সালাম চাচা ও নাসির চাচা কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্র থেকে বামফ্রন্ট সরকারের দেওয়া ঋণ নিয়ে গ্রামে প্রথম পোল্ট্রি করলেন। গ্রামের বাইরে মাঠে। তখন ঘরোয়া মুরগির মাংসের দাম ২০ টাকা। ছাগলের মাংসের নাম তখন মাটন হয়নি। দশ টাকা কিলো। এবার পোল্ট্রি এসে দাম হল ১৫ টাকা কেজি।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালএকটি টি-শার্ট - মোহাম্মদ কাজী মামুন
০৮ জুন ২০২৪ | ২০৪ বার পঠিতপুলসিরাত পার হয়ে যখন শেষমেষ তারা ঢুকলো অফিসটাতে, তখন দেখা গেল সেলিম ভিজলেও তার বসের মত কাকভেজা হয়নি, ফ্যানের বাতাসে একটুখানি বসলেই চলছে। ওদিকে বসের সামনে মেলে ধরা হয়েছে দীপুর টি-শার্টটা।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালবহিরাগত শিল্পী - Mani Sankar Biswas
০৭ জুন ২০২৪ | ১০১ বার পঠিতবহিরাগত শিল্পী হেনরি ডারগার
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালকিষেণজি মৃত্যু রহস্য - পর্ব ১২ - বিতনু চট্টোপাধ্যায়
০৭ জুন ২০২৪ | ২১২ বার পঠিত‘বুদ্ধদেববাবুর কনভয়ে ব্লাস্ট হয়েছে? একটা চ্যানেল দেখাচ্ছে।’ অফিস থেকে আসা এই এক লাইনের বার্তাই তখন যথেষ্ট ছিল। ড্রাইভারকে গাড়ি ঘোরাতে বলে সঙ্গে সঙ্গে ফোন করলাম মুখ্যমন্ত্রীর আপ্ত সহায়ক জয়দীপ মুখার্জিকে। ‘বুদ্ধদেববাবুর কনভয়ে ব্লাস্ট হয়েছে?’ ‘কিছু একটা হয়েছে। তবে ব্লাস্ট না। এসপি বলছে, ইলেকট্রিক ওভারহেড তার ছিঁড়ে একটা পুলিশের গাড়ির ওপর পড়েছে। তাতে একটু আগুন ধরে যায়। টাল সামলাতে না পেরে গাড়িটা উল্টে গিয়েছে। তাতে তিন-চারজন পুলিশ ইনজিওরড। তবে সিএমের কনভয়ে না, এটা ঘটেছে রামবিলাস পাসোয়ানের কনভয়ে।’
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালমহম্মদ সেলিম এবং লক্ষ্মীর ভাণ্ডার - সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায়
০৬ জুন ২০২৪ | ৮৯২ বার পঠিতমহম্মদ সেলিম বহু ক্ষেত্রেই সঠিক কথা বলে থাকেন। এবারও বলেছেন। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নিয়ে তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, "কেউ কেউ স্বঘোষিত বিপ্লবী আছে, তাদের আমরা বলি ফেসবুকে বেশি বিপ্লবীয়ানা করবেননা। কিন্তু করে। এখানে এমন একটাও সিপিএমের কাছ থেকে এক্সপেক্ট করতে পারোনা, যে, মহিলাদের সম্পর্কে বা এ ধরণের ভাতা সম্পর্কে অফিশিয়ালি ডিনাউন্স করছে। কেন করবে? আমরা আমাদের বামপন্থী আন্দোলন মানে হচ্ছে, গোট বিশ্বে আমরা চাই, সরকার ক্ষতিপূরণ হিসেবে, মানুষের যে অধিকার দিতে পারছেনা, তাকে কিছুটা অন্তত সাবসিডাইজ করবে। আর বাকি যারা এগুলো নিয়ে কটাক্ষ করছেন, তাঁরা বামপন্থী নন, তাঁরা হতে পারেন সমর্থক, আমাদের দায় আমাদের কথা তাঁদের কাছে নিয়ে যাওয়া, আমাদের মাধ্যমগুলো দিয়ে, সরাসরি তাঁদের কাছে গিয়ে। কেউ কেউ উগ্র সমর্থক আছেন, তাঁদের আমরা সমর্থক থাকতে বলব, উগ্রতা কমাতে বলব।" (শুনে শুনে লেখা, মোটামুটি হুবহু উদ্ধৃতি)।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালশিক্ষা না ভিক্ষা? - Anirban M
০৬ জুন ২০২৪ | ৪৯৩ বার পঠিতবাংলায় যে তৃণমূল প্রার্থীরা জিতলেন তাঁরা কী হেরে যাওয়া বাম প্রার্থীদের থেকে কম শিক্ষিত? এবং দেশে যে বামেরা জিতলেন তাঁরা কী বাংলার তৃণমূল বা বাম প্রার্থীদের থেকে কম বা বেশি শিক্ষিত? এই দুটি প্রশ্নের উত্তর বোঝার চেষ্টা তথ্যের ওপর ভিত্তি করে।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালহাঁটতে হাঁটতে - দ
০৬ জুন ২০২৪ | ২৬০ বার পঠিতঝলমলে সোশ্যাল মিডিয়া আর স্মার্টসিটির বাইরে কবে থেকে যেন হেঁটেই চলেছে আরেকটা ভারত। এতদিনে তাদের অন্তত নামটুকু নথিবদ্ধ থাকার কথা ছিল সরকারের কাছে। কথা ছিল, কিন্তু নেই আসলে, আর সেজন্য আমরা ন্যুনতম লজ্জিতও নই, প্রশ্নও করি না কেন অভিবাসী শ্রমিকদের তালিকা নেই সরকারের কাছে? কেন স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরেও গ্রামীণ মেয়েদের এত হাঁটতে হবে শুধুমাত্র জলের জন্য? বইটা আমাদের জ্বলন্ত এই প্রশ্নগুলোর মুখোমুখী দাঁড় করিয়ে দেয়। মনে করিয়ে দেয় ‘সুনাগরিক’এর দায়িত্ব পালন করি নি আমরাও।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালচললুম ঈর্ষাহীন দেবীর গৃহে - ১ - সমরেশ মুখার্জী
০৬ জুন ২০২৪ | ১৪৫ বার পঠিত"একা বেড়ানোর আনন্দে" - এই সিরিজে আসবে ভারতের কিছু জায়গায় একাকী ভ্রমণের অভিজ্ঞতা। এটি পর্ব - ২৬ … এই সিরিজের ৪নং পর্বে জনৈক নীল ২১.১০.২৩ লিখেছিলেন - “অনসূয়া দেবী যাত্রার কথা লিখবেন না?” বলেছিলাম - “লিখবো। সেও বেশ আনন্দময় অভিজ্ঞতা”। আরো নানা বিষয়ে লিখতে গিয়ে সময় হয়নি। এতোদিনে নীলের অনুরোধ রাখতে পারলাম। তবে আমার ছড়িয়ে ফেলা স্বভাব অনুযায়ী এই যাত্রা পথেও আসবে কিছু পার্শ্বপ্রসঙ্গ
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালহিন্দু মুসলমান -- একটি অ-জনপ্রিয় আলোচনা - Partha Banerjee
০৬ জুন ২০২৪ | ৩০২ বার পঠিতউগ্র সাম্প্রদায়িক ও নারীবিদ্বেষী হিন্দুত্ববাদী বিজেপি-আরএসএসের বিরোধিতার সঙ্গে সঙ্গে উগ্র সাম্প্রদায়িক ও নারীবিদ্বেষী এই মুসলমান শ্রেণীর সমান বিরোধিতা আমাদের করতে হবে। না হলে আমাদের কোনো বিশ্বাসযোগ্যতা সমাজে থাকবে না।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালতোমার বাস কোথা যে...-৫ - Nirmalya Nag
০৬ জুন ২০২৪ | ৩৬২ বার পঠিতডাক্তারের চেম্বারের দরজা ঠেলে ঢুকে বিনীতা দেখল ব্যাগ গোছাচ্ছে ইন্দ্রনীল। বিনীতাকে দেখে একটু অবাক হল সে। “কিছু বলবেন, ম্যাডাম?” “আপনি বললেন প্রতিটা দিনই ইমপরট্যান্ট। ওর কন্ডিশন ঠিক কতটা খারাপ?” “আরে না না। শুনুন, এই কন্ডিশন থেকে লোকে সুস্থ হয়েছে এমন অনেক এক্সাম্পল আছে।” “তার মানে কন্ডিশন খারাপ। কতটা? ও কি–” বিনীতার কথা থামিয়ে দিল ইন্দ্রনীল। “শুনুন, যা যা করার সব করা হবে। বললাম না প্রথমে সার্জারি, তারপর–” এবার ইন্দ্রনীলকে থামাল বিনীতা। “ও সব আপনি আগেই বলেছেন। এখন ক্লিয়ারলি বলুন, ও কি টার্মিনাল পেশেন্ট?” “দেখুন ম্যাডাম…” “আমি যথেষ্ট স্ট্রং, আপনি বলুন।” ইন্দ্রনীল চুপ করে থাকে।
- আরও বুলবুলভাজা ... আরও হরিদাস পাল ...
-
গুরুচণ্ডা৯-র গ্রাহক হোন
কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে গুরুচণ্ডা৯-র গ্রাহক হোন। গুরুচণ্ডা৯তে প্রকাশিত লেখাগুলি পেতে চাইলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যুক্ত হোন, অথবা, আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলটির গ্রাহক হোন।
- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই
- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... সুজয় দাস, প্রতিভা, Kishore Ghosal)
(লিখছেন... Prativa Sarker, Somnath Pal, Amit Chatterjee)
(লিখছেন... দ, হীরেন সিংহরায়, Kishore Ghosal)
(লিখছেন... অমিতাভ চক্রবর্ত্তী, অমিতাভ চক্রবর্ত্তী, অভিজিৎ চক্রবর্তী। )
(লিখছেন... SUSANTA GUPTA, Subhro Bhattacharyya, Abak Chittri)
- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন
(লিখছেন... )
(লিখছেন... যোষিতা, হীরেন সিংহরায়)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... )
(লিখছেন... )
- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... যোষিতা, musil, যোষিতা)
(লিখছেন... অরিন, অরিন, অমিতাভ চক্রবর্ত্তী)
(লিখছেন... সমরেশ মুখার্জী, Kishore Ghosal, syandi)
(লিখছেন... পাপাঙ্গুল, দীপ, দীপ)
(লিখছেন... kk, দীপ, dc)
- কি, কেন, ইত্যাদি
- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...
- আমাদের কথা
- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...
- বুলবুলভাজা
- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...
- হরিদাস পালেরা
- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...
- টইপত্তর
- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...
- ভাটিয়া৯
- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...