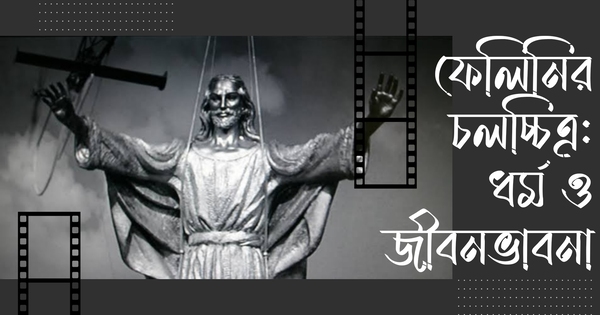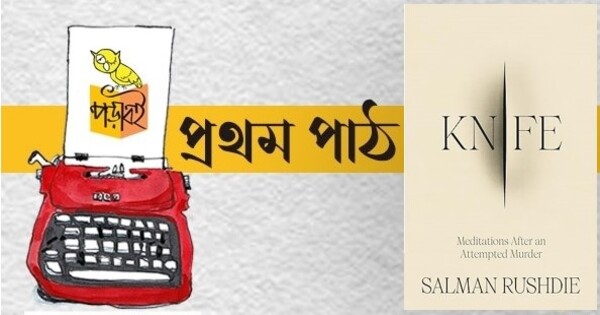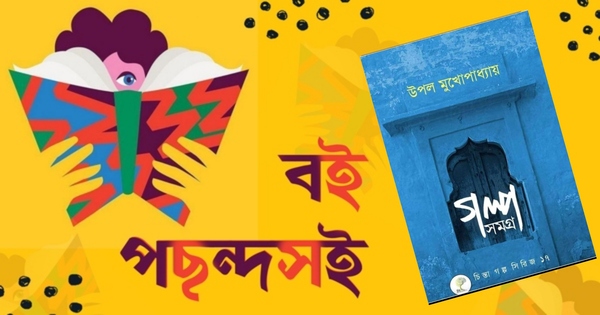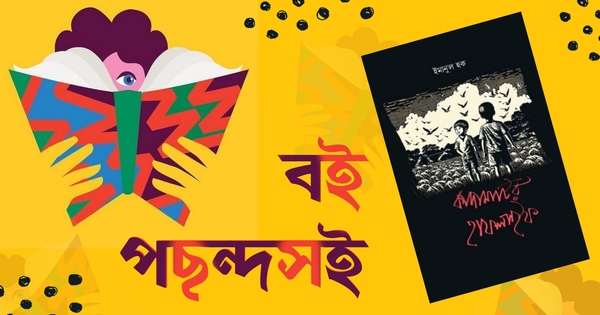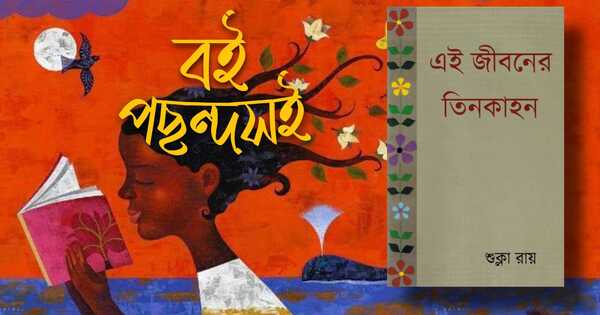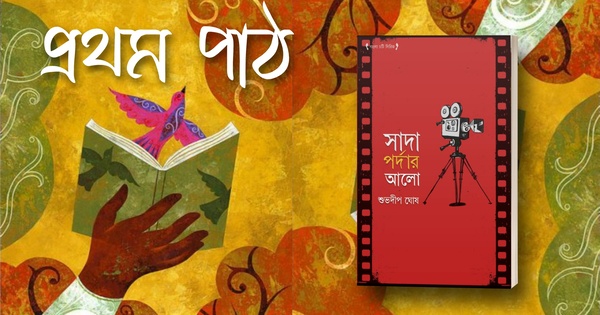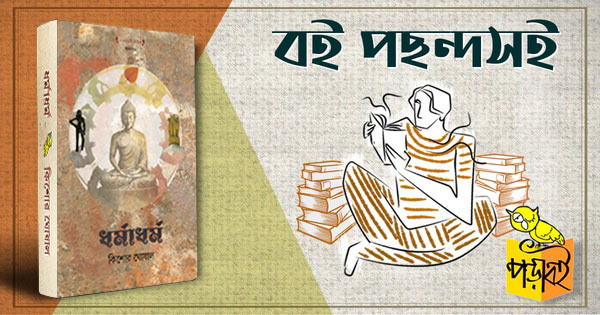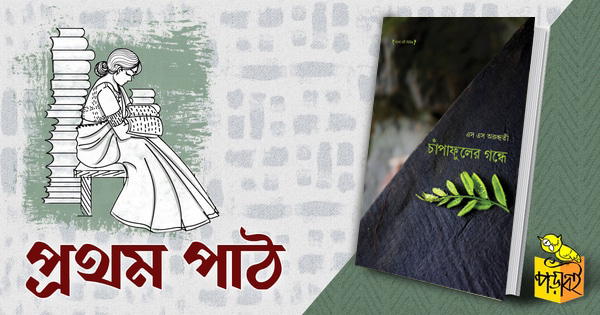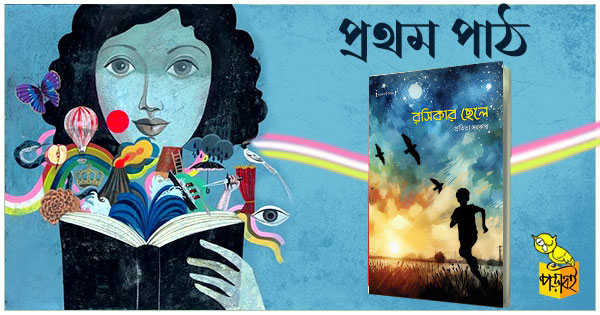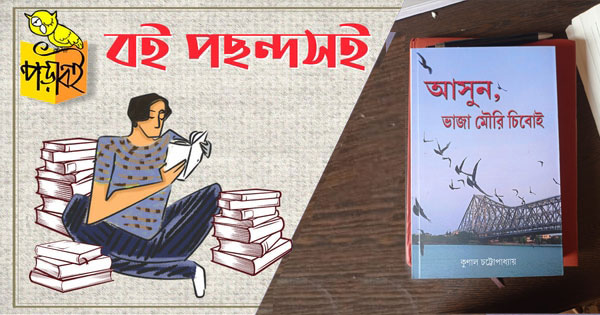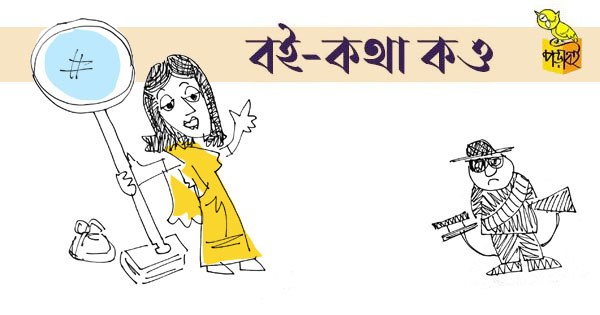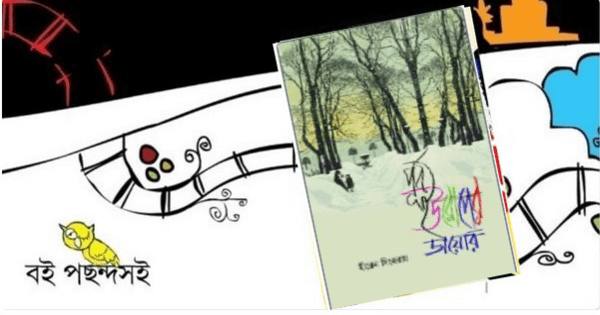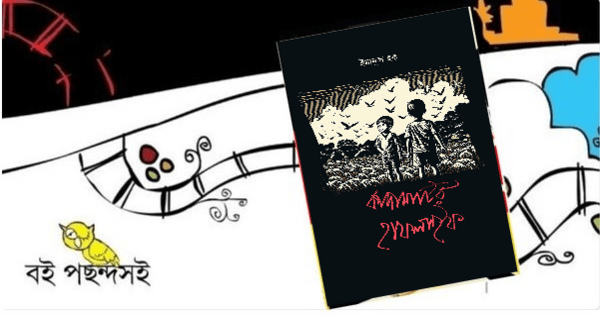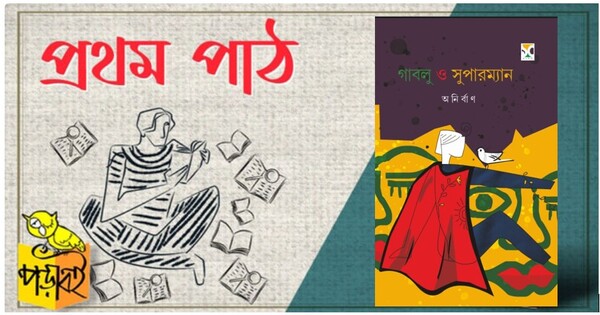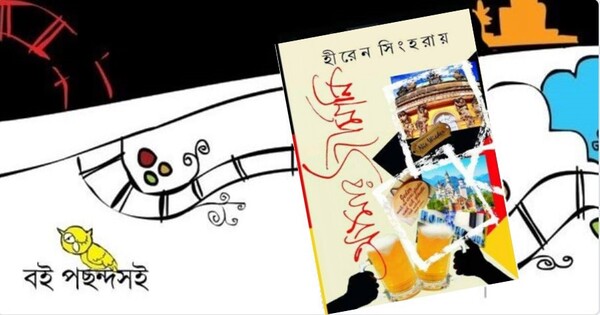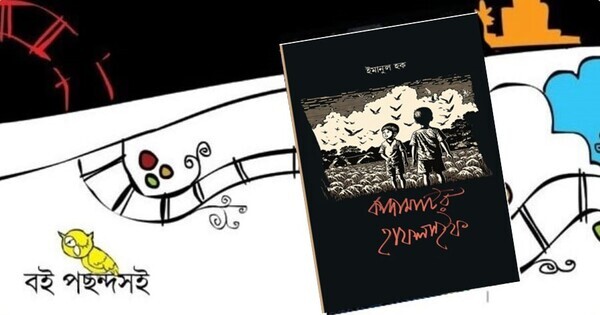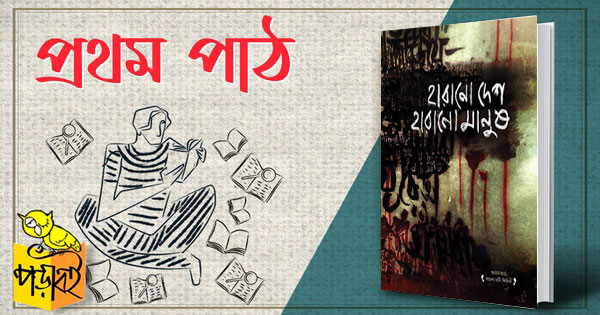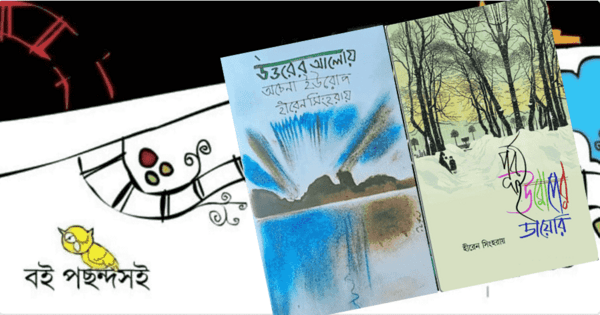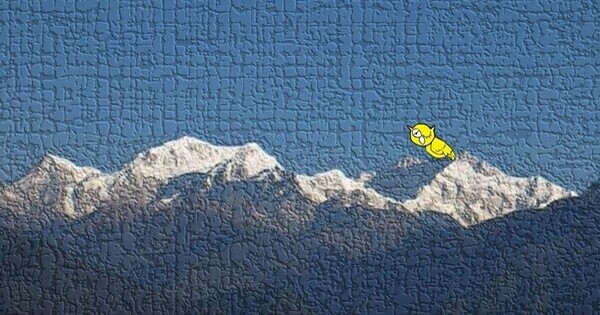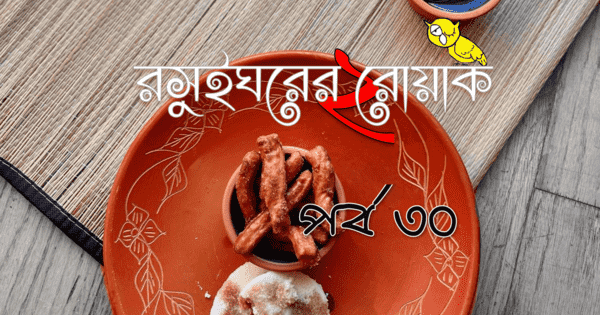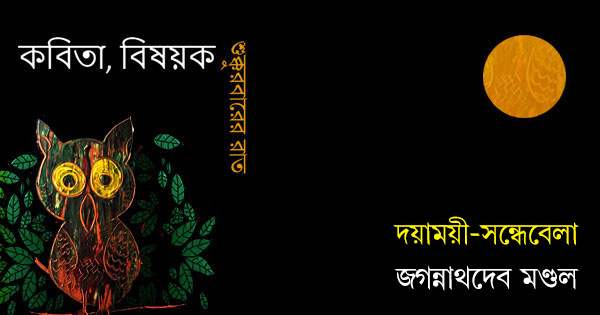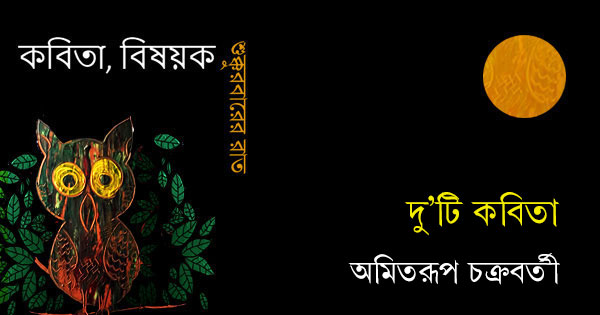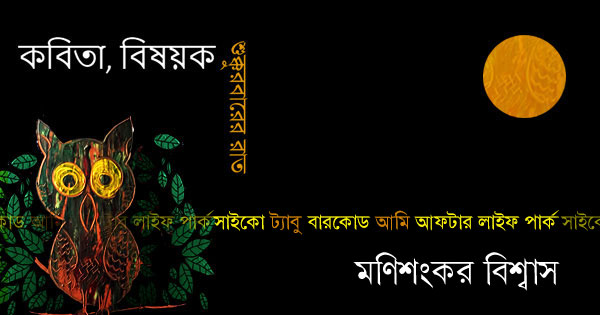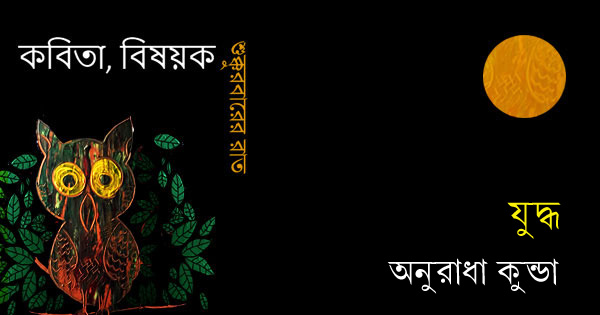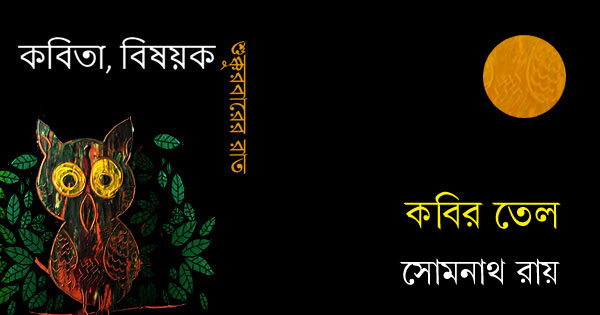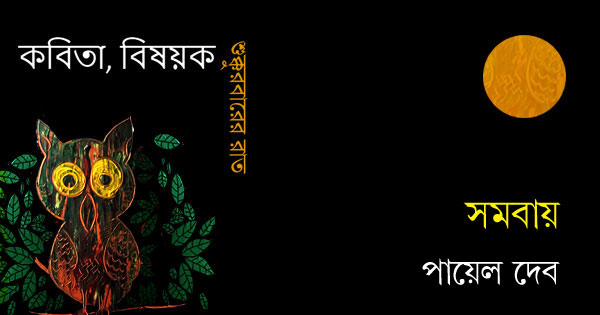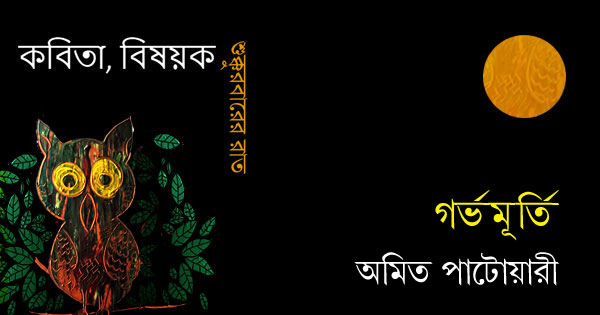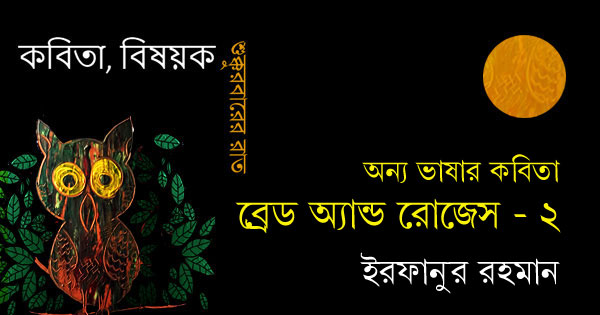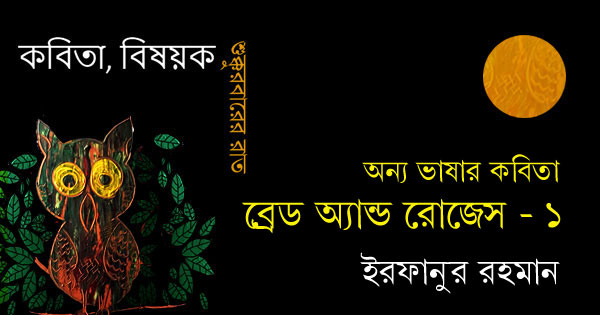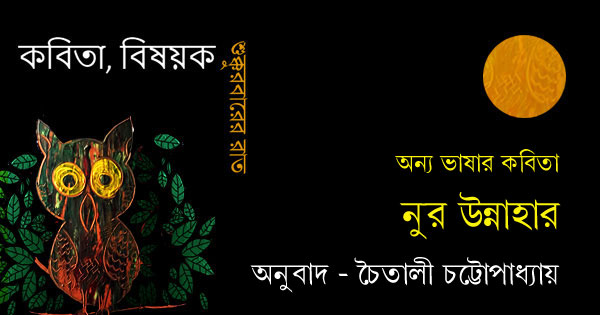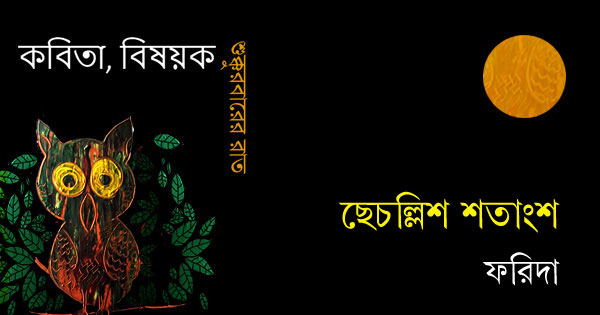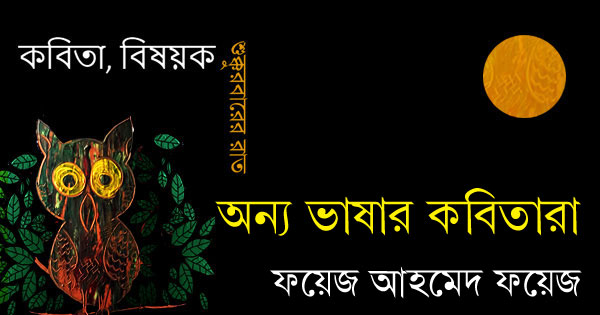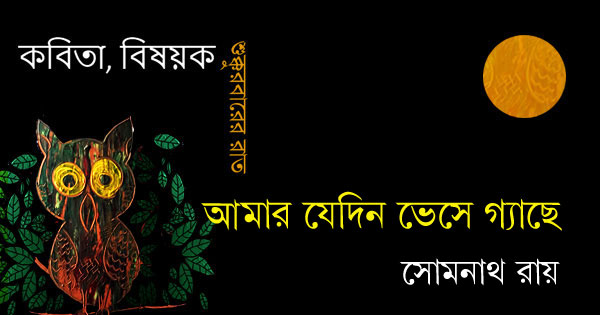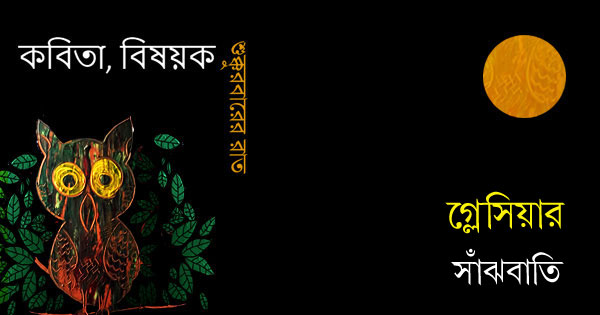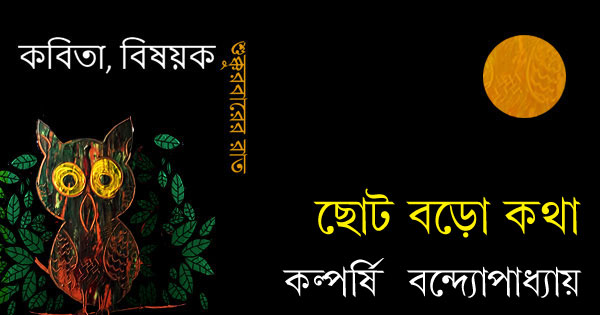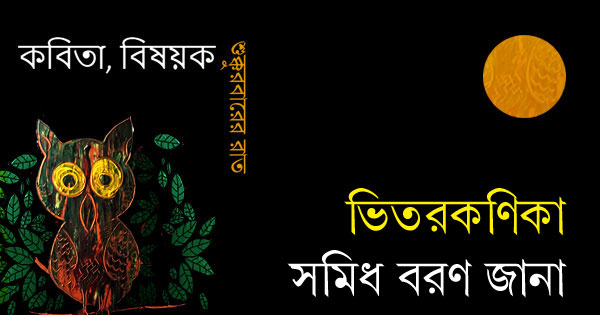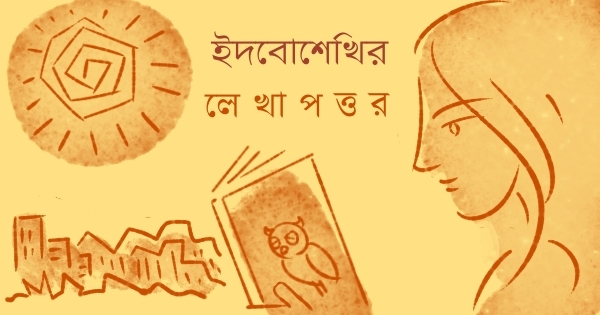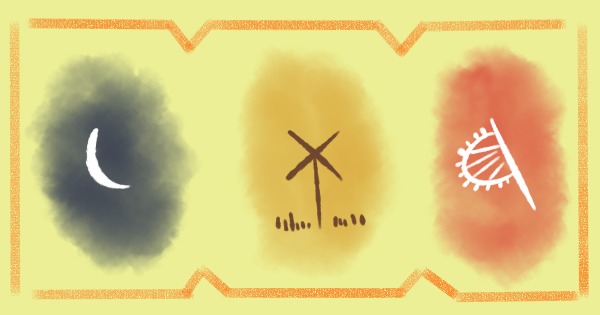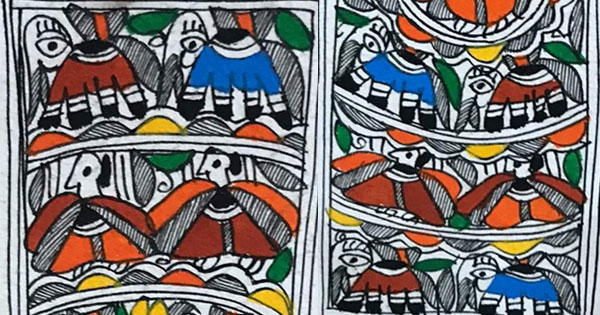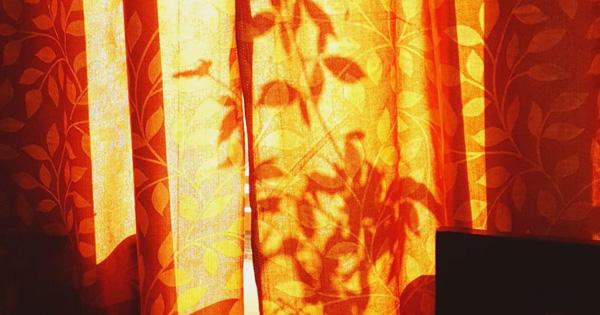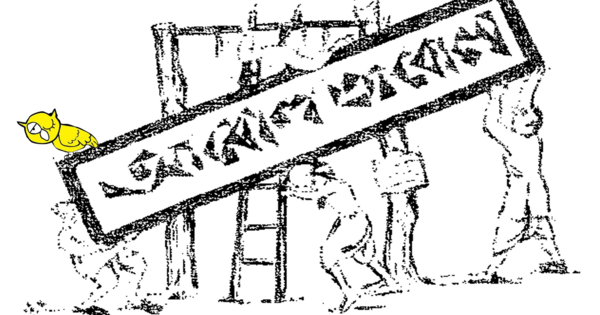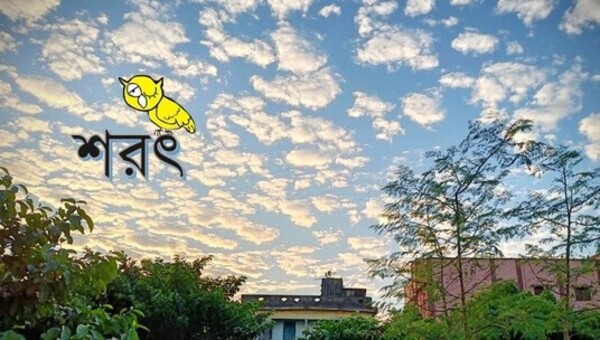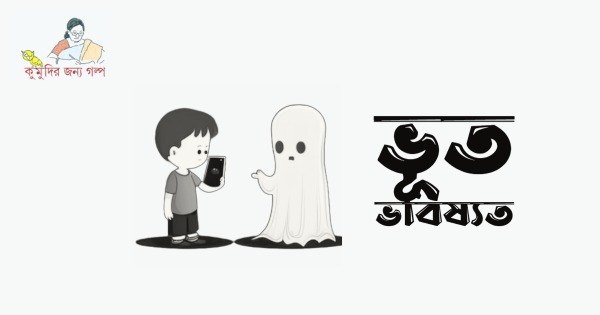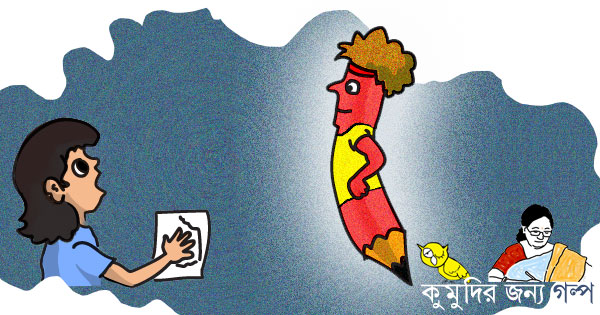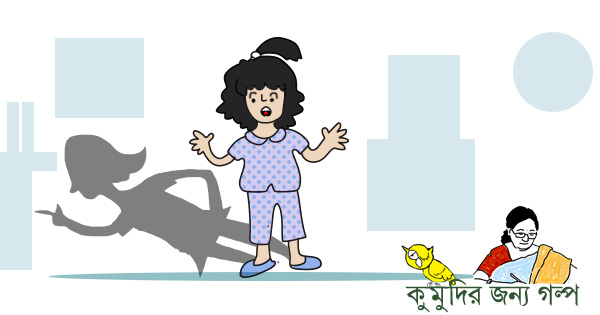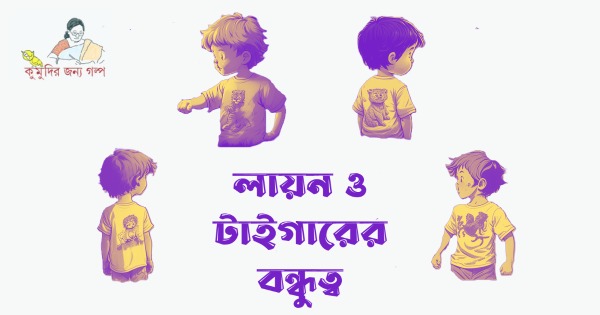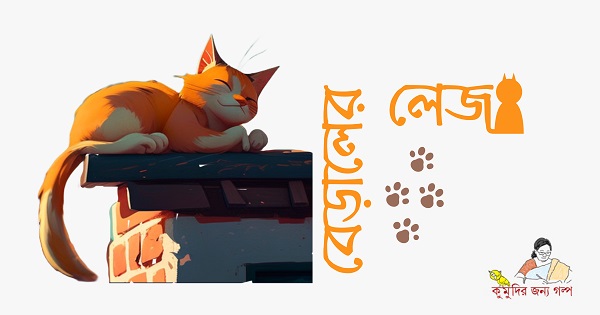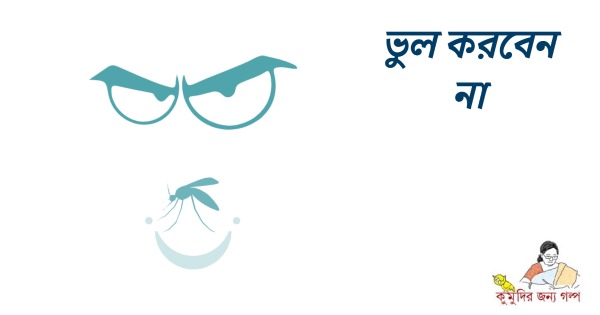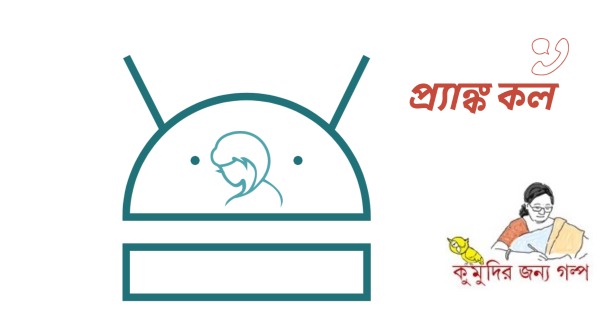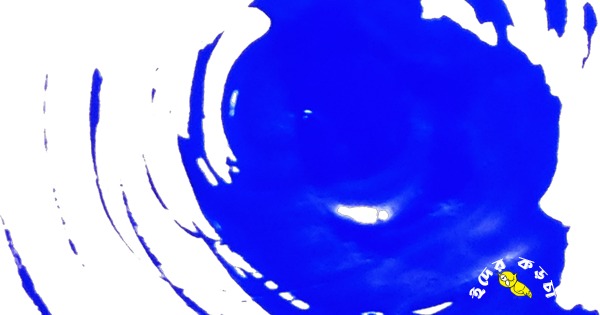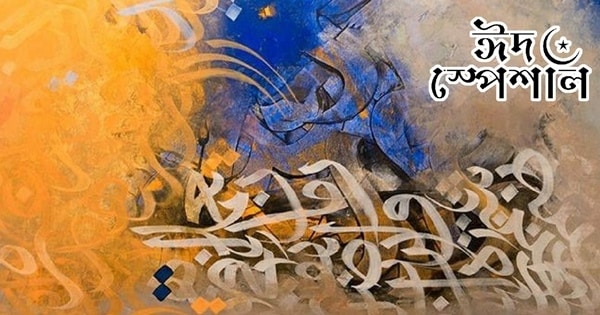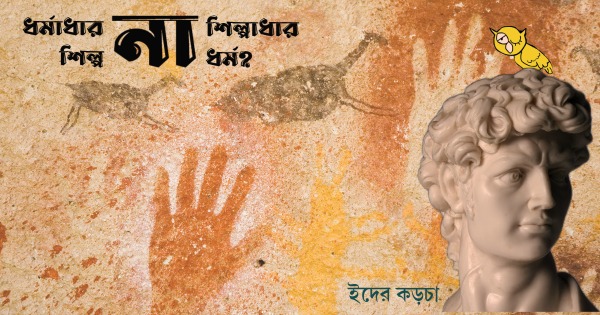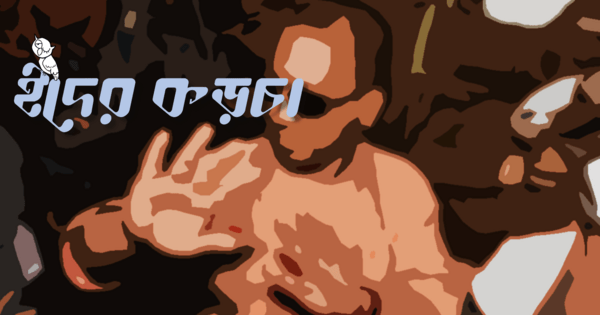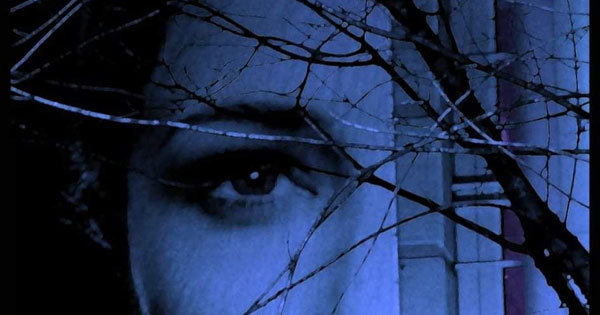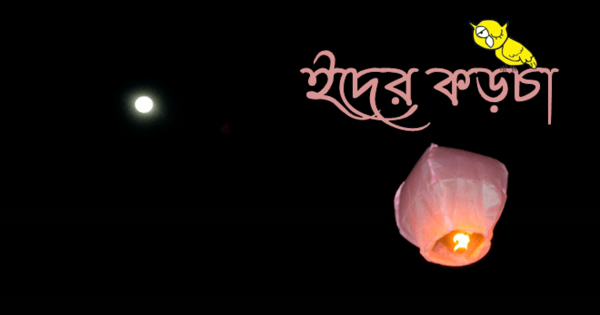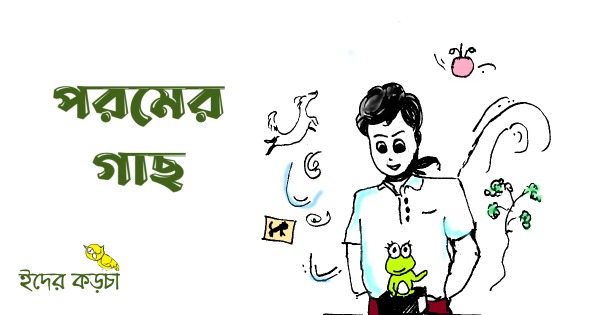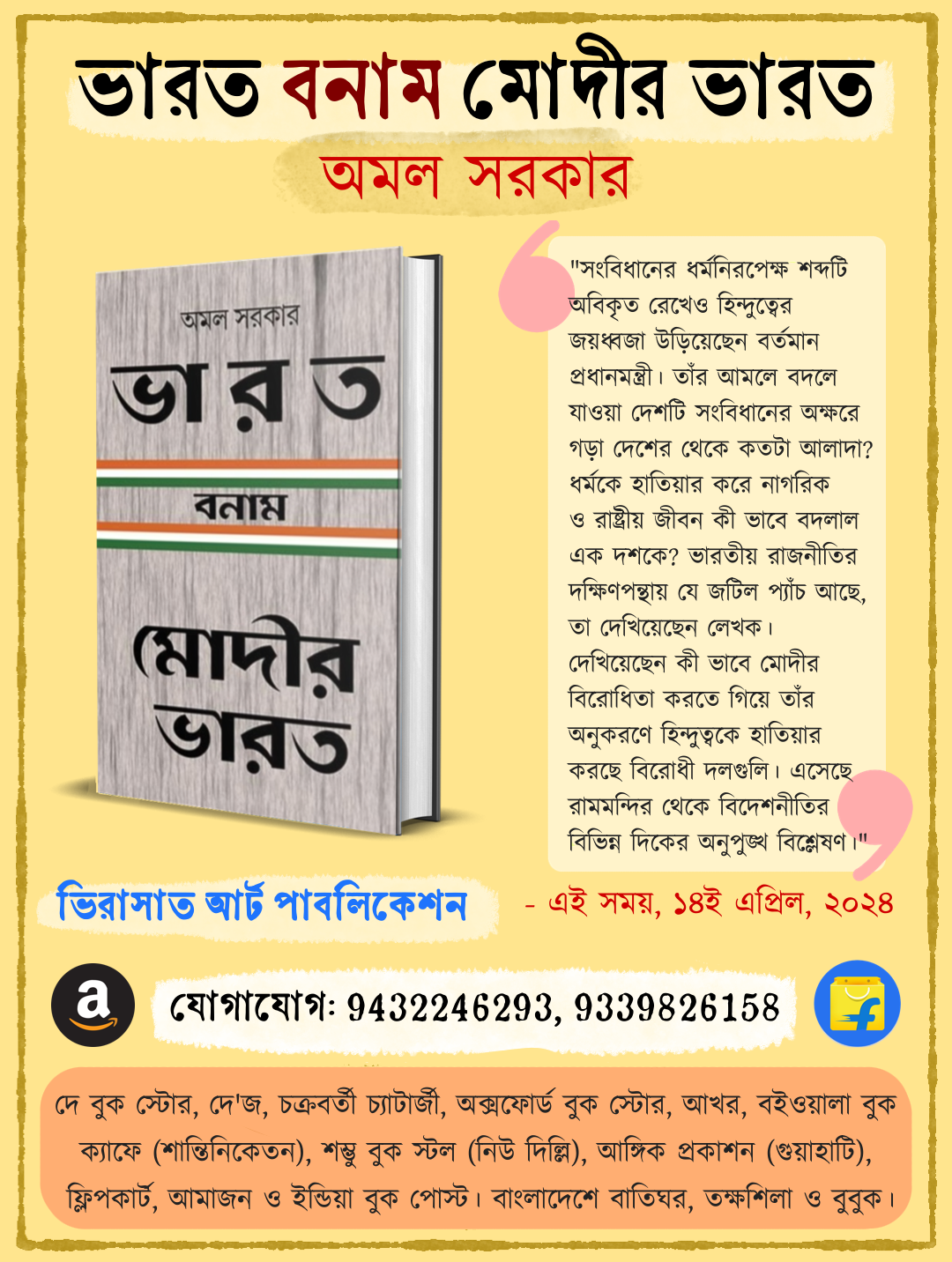তাজা বুলবুলভাজা...
বিপ্লবের আগুন - পর্ব সাত - কিশোর ঘোষাল | ছবি: রমিত চট্টোপাধ্যায়৭পরের দিন খুব ভোরবেলাতেই ভল্লার ঘুম ভেঙে গেল। আজ বেশ সুস্থ বোধ করছে সে। শরীরের ব্যথা, বেদনা – গ্লানি নেই বললেই চলে। বিছানায় উঠে বসল, তারপর ধীরে ধীরে ঘরের বাইরে এল। ভোরের আলো সবে ফুটেছে, বাইরের গাছপালার ডালে ডালে পাখিদের ব্যস্ততা টের পাওয়া যাচ্ছে তাদের কলকাকলিতে। হাওয়ায় সামান্য শিরশিরে ভাব। বিছানায় ফিরে গিয়ে সে গায়ের চাদরটা তুলে নিয়ে গায়ে জড়াল। দড়ি থেকে টেনে নিল গামছাটা – কষে বেঁধে নিল মাথায়। তারপর প্রশস্ত অঙ্গন পেরিয়ে সন্তর্পণে এগিয়ে চলল পথের দিকে। কঞ্চি দিয়ে বানানো, বেড়ার পাল্লা খুলে সবে পথে নামতে যাবে, কমলি ডাক দিল, “অ্যাই, এই কাক ভোরে কোথায় চললি রে? পালাবার ফিকির বুঝি? এখনো তোর শরীর পুরোপুরি সারেনি…”। কমলির হাতে জলভরা ঘটি। ভল্লা ঠোঁটে আঙুল রেখে কমলিকে ফিসফিস করে বলল, “প্রধানমশাই শুনতে পেলে এখনই হৈচৈ বাধাবে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে শরীরে এবার ঘুণ ধরে যাবে। একটু ঘুরেঘেরে আসি…গাঁয়ের লোকদের সঙ্গে চেনা পরিচয় করে আসি…। আমি পালাইনি রে, মা। প্রধানমশাইকে আমি ভয় পাই নাকি? ভয় করি তোকে। তুই না তাড়ালে, আমি এ বাড়ি ছেড়ে, এই গ্রাম ছেড়ে সহজে নড়ছি না…এই বলে দিলাম, মা”।ভল্লার চোখের দিকে তাকিয়ে কমলির চোখ ছলছল করে উঠল। বছর দশেক আগে তাঁর হারিয়ে যাওয়া দুই ছেলের বড়টি যেন ফিরে এসেছে তাঁর কাছে। কমলির প্রৌঢ় দুই পয়োধর আচমকাই যেন ভারি হয়ে ব্যথিয়ে উঠল। অস্ফুট স্বরে বললেন, “তার নাম ছিল বুকা – সে আজ থাকলে ঠিক তোর মতই হত…”ভল্লা বলল, “আমিই তো সেই…নিজের ছেলেকে চিনতে পারিস না, কেমন মা তুই?” চোখ আর নাক কুঁচকে ভল্লা হাসল। কমলি চোখের জল এড়াতে মুখ ঘুরিয়ে বললেন, “একটু দাঁড়া, নাচ দুয়োরে জলছড়া দিই, তারপর বেরোস…নইলে অমঙ্গল হয়…বেশি দেরি করিস না ফিরতে…”। পথে নেমে ভল্লার মনে পড়ল, সে এই গাঁয়ে ঢুকেছিল বাঁদিকের রাস্তা দিয়ে। অতএব গাঁয়ে যেতে গেলে নিশ্চয়ই ডাইনে যেতে হবে। সে ডানদিকেই হাঁটা দিল ধীরে সুস্থে। পথের পাশে একটা বাবলা গাছ পেল। খুব সাবধানে কাঁটা সামলে ছোট্ট একটা ডাল ভেঙে, মুখে নিয়ে চিবোতে লাগল। নিমের ডালের থেকে তার বাবলার ডালই পছন্দ। মন্থর পায়ে চলতে চলতে সে দেখল পথের দুপাশেই বাড়ি – তবে একটানা লাগাতার নয়। দুই বাড়ির মাঝখানে কোথাও খালি জমি – কোথাও পুকুর। বাড়িগুলি খুবই সাধারণ। বাঁশের বাতায় পুরু করে মাটি লেপে দেওয়াল। কাঠের কাঠামোর ওপর শালপাতার ছাউনি। ঝড়ঝাপটা, বৃষ্টি-বাদলায় এসব বাড়ি মোটেই নিরাপদ নিশ্চিন্ত আশ্রয় হতে পারে না। বেশ কিছু বাড়িতে ছাগলের খামার রয়েছে। সকাল বেলা সব বাড়ি থেকেই বেরিয়ে আসছে ছাগলের দল। কারো কম – চারপাঁচটা, কারো কারো বেশি পনের-বিশটা। দুটো ছোঁড়া হাতে পাঁচন বাড়ি নিয়ে তাদের জড়ো করছে। তারপর খেদিয়ে নিয়ে যাচ্ছে চারণ জমির দিকে। ভল্লা ছোঁড়াদুটোকে জিজ্ঞাসা করল, “শুধুই ছাগল, গরুবাছুর নেই?”ছোঁড়াদুটো কথা বলল না, শুধু ঘাড় নেড়ে বলল, না। “গ্রাম থেকে কতদূরে, রে? যেখানে এদের চড়াতে নিয়ে যাস?” ছোঁড়াদুটোর একজন হাত তুলে দেখাল, বলল, “হোই তো হোথা”। অন্যজন জিজ্ঞাসা করল, “তুমি কমলিমায়ের বাড়ি এসেছ না? কোথা থেকে এসছ? যাবে কোথায়?”ভল্লা ওদের মাথায় হাত রেখে বলল, “অনেকদূরের শহর থেকে এসেছি...তোদের সঙ্গে দেখা করতে, এখানে থাকতে...এখন আর কোত্থাও যাবো না আমি”।ওদের তাড়া আছে, ভল্লার নেই। ছেলেদুটো ছাগলের পাল নিয়ে এগিয়ে গেল। ভল্লা দাঁতন চিবোতে চিবোতে বুঝতে লাগল, গ্রামের পরিস্থিতি। গ্রামের আঁকাবাঁকা পথ ধরে সে ধীরে ধীরে চলতে লাগল। এখনও পর্যন্ত কোন বাড়িতেই সে শস্যের গোলা দেখতে পেল না। এমনকি গ্রামপ্রধান জুজাকের বাড়িতেও সে শস্যগোলা দেখেনি। জুজাকের বাড়ির যে ঘরে রয়েছে, সে ঘরেরই এক কোণায় রাখা তিনটে বড় মাটির জালায় ভুট্টা আর জোয়ারের দানা দেখেছে। সে দিয়ে সারাবছরের খোরাক হয়ে যায়? জুজাক আর কমলিমায়ের মাত্র দুজনের সংসার…তাতেও সারাবছর চলতে পারে না। তাছাড়া শুধু পেটে খেলেও তো হয় না। তেল, নুন, কিছু কিছু মশলা, ধুতিশাড়ি, শীতের চাদর, কাঁথা-কম্বল সে সব কিনতেও তো ভরসা ওই শস্যদানাই! তার ওপর আছে শখ আহ্লাদ, পালা-পার্বণ, দায়-দৈব…। রাজধানী শহরের বিত্তবান মানুষের কাছে শস্যদানা থাকে না। তাদের থাকে কড়ি, রূপোর মুদ্রা, সোনার মুদ্রা। সেই মুদ্রা দিয়ে জগতের সব কিছু কিনে ফেলা যায় – ঘরবাড়ি, মূল্যবান কাপড়চোপড়, গয়না-অলংকার, বিলাসব্যসন, সুরা… কি নয়? ভল্লার মনে পড়ল রাজশ্যালক রতিকান্তর কথা। রাজার অনুগ্রহে প্রতিপালিত নিষ্কর্মা, লম্পট লোকটা কত অর্থের অনর্থক অপচয় করে চলেছে প্রত্যেকদিন। অথচ এইখানে এই গ্রামে কী নিদারুণ কঠিন পরিস্থিতি।হাঁটতে হাঁটতে ভল্লা গিয়ে পৌঁছল অনেকটা উন্মুক্ত এক জমিতে। বাঁদিকে বিশাল এক জলাশয়। জলাশয়ের তিনদিকে ঘন গাছপালার সারি আর ঝোপঝাড়। আর সামনেই পাথরে বাঁধানো ঘাট। সেই ঘাট থেকে কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রাচীন এক অশ্বত্থ গাছ। শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে নিবিড় ছায়াময় করে তুলেছে বৃক্ষতল। সেখানে বেশ কিছুটা জায়গা জুড়ে পাথর বিছানো বসার জায়গা। ভল্লার মনে হল, পাথরের ওই আসনগুলি গ্রামের মাতব্বর পুরুষদের বিশ্রম্ভালাপের জায়গা। অপরাহ্ণে হয়তো অনেকেই আসে - কথাবার্তা, শলা-পরামর্শ, পরনিন্দা-পরচর্চা সবই চলে। গ্রামের পালা-পার্বণে উন্মুক্ত এই জমিতেই হয়তো গ্রামবাসীরা সমবেত হয়। হইহুল্লোড়, নাচ-গান করে। ভল্লা সেই জলাশয়ের ঘাটে গিয়ে দাঁড়াল। স্বচ্ছ নির্মল জলের ওপর ছায়া পড়েছে তিনপাশের গাছপালা আর মাথার ওপরের সুনীল আকাশের। জলাশয়ের বিস্তার এতই বড়ো, জলের উপরে তিরতিরে তরঙ্গ উঠছে, প্রভাতী বাতাসের স্পর্শে। ভল্লা ঘাটে নেমে জলস্পর্শ করল, মুখ ধুয়ে, মুখে চোখে জল দিল। কিছুটা জল পানও করল। চাদরে মুখ মুছে ঘাটেই বসল।কিছুক্ষণ আগেই সূর্যোদয় হয়েছে তার সামনে, কিছুটা ডানদিকে। ওদিকে ছোট্ট টিলা আছে একটা। ভল্লার মনে পড়ল, এই গ্রামে ঢোকার মুখে সে একটা সরোবরের সামনে দাঁড়িয়েছিল। তার যতদূর ধারণা সেই সরোবরটা রয়েছে ওই টিলার কোলেই। ওখান থেকে আধক্রোশ মত পথ নেমে সে গ্রামে ঢুকেছিল। তার মানে সে এখন যে দীঘির সামনে বসে আছে, তার ওপারের ঝোপঝাড় বেয়ে ওই টিলার পায়ের কাছেই পাওয়া যাবে রাজপথ। কিন্তু ভল্লার মনে হল, সরোবরের পাড় ধরে যে পথে সে নেমে এসেছিল, সে পথ নেহাতই পায়ে চলা পথ। ও পথে গোরু কিংবা ঘোড়ার গাড়ির পক্ষে ওঠা-নামা সম্ভব নয়। অবশ্য দক্ষ অশ্বারোহী ওপথে যাওয়া আসা করতে পারবে। তাহলে এই গ্রামে ঢোকার জন্যে সদর রাস্তাটি কোনদিকে? ভল্লাকে সেটা জানতে হবে। নোনাপুর গ্রাম এই রাজ্যের সীমান্তবর্তী গ্রাম। অর্থাৎ এই গ্রামের পশ্চিম দিকে রয়েছে প্রতিবেশী রাজ্যের সীমানা। সেই সীমানা এই গ্রাম থেকে কতদূরে? সাধারণতঃ কোন রাজ্যেরই সীমান্ত বরাবর কোন বসতি থাকে না। প্রতিবেশী দুই রাজ্যই জনহীন দূরত্ব বজায় রাখে। অতএব সেই অঞ্চলটি বনাকীর্ণ এবং হয়তো দুর্গম। যদিও ভল্লা জানে, প্রশাসনিক অনুমোদন না থাকলেও সাধারণ জনগণের কিছু অংশ এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে যাতায়াত করে থাকে। দৈনিক শ্রমের বিনিময়ে কিছু উপার্জনের আশায়। এবং নিয়ম বহির্ভূত কিছু বাণিজ্যিক প্রয়োজনে। নোনাপুরের কথা সে যেমন শুনেছে এবং আজ সকালে গ্রামের পরিস্থিতি যতটুকু সে উপলব্ধি করেছে – তাতে পড়শি রাজ্যের সঙ্গে এই গ্রামের যোগাযোগ থাকা খুবই স্বাভাবিক।“এই যে ছোকরা…”। পিছন থেকে পুরুষ কণ্ঠের আচমকা ডাকে ভল্লার ভাবনা সূত্র ছিন্ন হল। পিছন ফিরে দেখল, ঘাটের প্রথম ধাপে জনৈক মধ্যবয়সী পুরুষ তাকে ডাকছে, “সেই থেকে ঘাটে বসে কী করছ হে? জান না, সকালে গ্রামের মেয়েরা ঘাটে আসে নানান কাজে…”। মধ্যবয়সী পুরুষের পিছনে চার-পাঁচজন নারী, মাটির কলসি কাঁখে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সকলেরই মুখভাবে বিরক্তি। ভল্লা দ্রুত উঠে এল ঘাট থেকে, করজোড়ে বিনীত স্বরে বলল, “আমাকে মার্জনা করবেন, আমার অন্যায় হয়েছে। আসলে বিগত কয়েকদিন আমার জীবনের ওপর দিয়ে যে প্রবল ঝড় বয়ে গেল, সেই সব কথাই ভাবছিলাম…এই জায়গাটা এতই নিরিবিলি আর সুন্দর…”। মধ্যবয়সী পুরুষ বলল, “তোমাকে তো বিদেশী মনে হচ্ছে…তুমিই কী সেই যুবক যে ভয়ংকর অসুস্থ অবস্থায় গ্রামপ্রধান জুজাকের বাড়িতে এসেছ?”ভল্লা আগের মতোই সবিনয়ে বলল, “আজ্ঞে হ্যাঁ আমিই সেই হতভাগ্য যুবক”। মধ্যবয়সী সেই পুরুষ ভল্লার কাঁধে হাত রেখে বলল, “তোমার কথা অনেক শুনেছি। এস, আজ তোমার সঙ্গে আমাদের পরিচয়টা সেরে নেওয়া যাক”। মধ্যবয়সী সেই পুরুষের পিছনে পিছনে ভল্লা উপস্থিত হল প্রাচীন সেই অশ্বত্থ গাছের কাছে। ভল্লা দেখল সেখানে আরও তিনজন মধ্যবয়সী এবং দুজন প্রায় বৃদ্ধ পুরুষ বসে আছে। সকলেরই কৌতূহলী দৃষ্টি ভল্লার দিকে। ভল্লার সঙ্গী পুরুষ পাথরের আসনে বসতে বসতে সকলের দিকে তাকিয়ে বলল, “এই সেই যুবক, মারাত্মক অসুস্থ অবস্থায় জুজাকের ঘরে যে আশ্রয় নিয়েছিল। কবিরাজমশাইয়ের চিকিৎসায় এখন মনে হয় সুস্থ হয়ে উঠেছে”।বৃদ্ধদের মধ্যে একজন বলল, “তা তোমার নামটি কি হে?”ভল্লা মাটিতে উবু হয়ে বসে বলল, “আজ্ঞে আমার নাম ভল্লা”। মধ্যবয়সীদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করল, “বলি ভল্ল-টল্ল ছুঁড়তে পারো? নাকি শুধু নামই সার”?খুব বিনীত স্বরে ভল্লা বলল, “আজ্ঞে, একটু আধটু পারি, তবে সে বলার মতো কিছু নয়...”।আরেকজন মধ্যবয়সী বলল, “তা তুমি পাথরের আসন ছেড়ে মাটিতে বসলে কেন?”“ছি ছি, আপনারা এই গ্রামের গুরুজন, আপনাদের সঙ্গে একাসনে বসাটা আমার মতো সামান্য জনের পক্ষে ন্যায্য হতে পারে না”।“তা কোথা থেকে আসা হচ্ছে”? “আজ্ঞে সেই সুদূর কদম্বপুর থেকে। তবে আমার বাড়ি কদম্বপুর থেকে দূরের এক গ্রামে। রাজধানীতে বাস করি কর্মসূত্রে”। “তা রাজধানীতে কী রাজকার্য করা হয়?” একজন কিছুটা বিদ্রূপের সুরেই জিজ্ঞাসা করল।লাজুক হেসে ভল্লা বলল, “আজ্ঞে রাজকার্য করার মতো বিচার-বুদ্ধি কিংবা বিদ্যা কি আর আমার আছে? গায়েগতরে কিছু বল আছে...সেই সুবাদে রাজধানীর অজস্র নগররক্ষীর মধ্যে আমিও একজন”। ভল্লাকে যে ডেকে এনেছিল, সে জিজ্ঞাসা করল, “তোমার কথা বিশ্বাস করা গেল না, হে। নগররক্ষীই যদি হবে – তবে চোরের মার খেয়ে রাজধানী থেকে পালিয়ে এখানে এসে উপস্থিত হলে কেন?”কয়েকজন মাথা নেড়ে সায় দিল, দুজন বলল, “ঠিক কথা। সত্যি কথা বল, না হলে এই গ্রাম থেকে তোমাকে আজই বিদেয় করা হবে...”। ভল্লা বিনীত সুরে কিন্তু দৃঢ় স্বরে বলল, “আজ্ঞে, শুধু এই গ্রাম নয়, এই রাজ্য থেকেই আমার বিদেয় হওয়ার কথা”। উপস্থিত সকলেই উত্তেজিত হয়ে বললেন, “তার মানে? নির্বাসন দণ্ড? তুমি অপরাধী?”“আজ্ঞে হ্যাঁ। নির্বাসন দণ্ড। কিন্তু আমি অপরাধী এ কথা আমি স্বীকার করব না। আমার মনে হয়, আমার কথা শুনলে আপনাদের বিচারে আপনারাও আমাকে অপরাধী বলতে পারবেন না”।কৌতূহলী ছয় পুরুষ নিজেদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করল, তারপর এক বৃদ্ধ বলল, “আমাদের বিচারে কী আসে যায়? আমরা তো প্রশাসনিক রায়ের ঊর্ধে নই। অতএব তোমার নির্বাসন দণ্ডের নিরসন আমরা করতে পারব না। কিন্তু তোমার কথা শোনার কৌতূহলও হচ্ছে। আমরা রাজধানী থেকে বহুদূরের বাসিন্দা – রাজধানীর পরিস্থিতি সম্পর্কে আমরা প্রায় কিছুই জানি না। প্রত্যেক বছর কর আদায়ের জন্য যে করাধ্যক্ষ আমাদের অঞ্চলে দু-তিনমাসের অস্থায়ী শিবির স্থাপনা করে - তার থেকে এবং তার অধস্তন কর্মীদের থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু সংবাদ পাই। তুমি বল হে ছোকরা। সত্যি মিথ্যে কিছু তো সংবাদ আমরা শুনতে পাবো”।মাথা নীচু করে ভল্লা কিছুক্ষণ বসে রইল। সে ঘাড় ঘুরিয়ে না তাকালেও অনুভব করল, তার পিছনেও অনেকে এসে দাঁড়িয়েছে। এবং তার অনুমান তাদের অধিকাংশই তার সমবয়স্ক যুবক এবং তরুণ। নচেৎ তারাও সামনে আসত এবং হয়ত বয়স্কদের পাশে বসত কিংবা দাঁড়াত। এই অনুভবে ভল্লা নিশ্চিন্ত হল। এরকম আসরে তার বিবরণ শোনাতে পারলে, তাকে একই কাহিনী বারবার বলে কালক্ষয় করতে হবে না। সে নিশ্চিত তার ঘটনার কথা অচিরেই এই গ্রামে তো বটেই – আশেপাশের গ্রামগুলিতেও প্রচার হয়ে যাবে। সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে, ভল্লা তার বিবরণ বলতে শুরু করল। সেদিনের মধ্যাহ্নের রাজপথে সেই বানজারা রমণীদের কথা। তাদের সঙ্গে রাজশ্যালক লম্পট রতিকান্তর দুরাচারের কথা। নগররক্ষী হয়ে তার দায়িত্বের কথা। এবং ক্রুদ্ধ হয়ে রাজশ্যালকের দিকে ভল্ল ছোঁড়ার কথা, সবই বলল। বর্ণনার শেষে বলল, “বিশ্বাস করুন, রাজশ্যালককে বিদ্ধ করে ওই স্থানেই আমি নিধন করতে পারতাম। করিনি, ভীরু কাপুরুষ লম্পট রাজশ্যালককে আমি শুধু ভয় পাইয়ে নিরস্ত করতে চেয়েছিলাম। রাজশ্যালকের দেহরক্ষীরা আমাকে বন্দী করল। নির্মম অত্যাচার করে উপনগরকোটালের কাছে আমায় সঁপে দিল। আমার প্রতি উপনগরকোটাল কিছুটা স্নেহাসক্ত ছিলেন, রাত্রের অন্ধকারে তিনিই আমাকে রাজ্যত্যাগ করতে আদেশ করলেন। নচেৎ পরেরদিন আমার হয়তো প্রাণদণ্ডও হতে পারত। প্রশাসনিক বিচারে আমার নির্বাসন দণ্ড হয়েছে। সে দুর্ভাগ্য আমাকে মাথা পেতে স্বীকার করে নিতে হয়েছে। কিন্তু এ কথা চিন্তা করে আনন্দও পাচ্ছি যে, লম্পট রাজশ্যালক যে শিক্ষা পেয়েছে, অন্ততঃ কিছুদিনের জন্যে সে নিজেকে সংযত রাখবে। আর ওই বানজারা রমণীদের মতোই আরও অনেক কুলনারী, কুমারী কন্যারাও ওই লম্পটের গ্রাসমুক্ত থাকবে”।অন্য এক বৃদ্ধ মন্তব্য করল, “ওই রাজশ্যালকের চরিত্রহীনতার কথা আমাদের কানেও এসে পৌঁচেছে। কিন্তু আমাদের রাজা তো মহান। বিচক্ষণ, প্রজারঞ্জক, দূরদর্শী। তিনি তাঁর এই শ্যালকটিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না?”ভল্লা বিনয়ে হাতজোড় করে বলল, “অনেক কথাই কানে আসে। কিন্তু আপনারা প্রাজ্ঞ-গুরুজন, আমি অতি নগণ্য এক রাজকর্মী। আপনাদের সামনে আমার মতো ছোট মানুষের মুখে বড়ো কথা মানায় না। আমাকে ক্ষমা করবেন”।পিছন থেকে কেউ একজন বলল, “আপনার আর ভয় কি? আমাদের এই গ্রাম শেষেই এক প্রহরের হাঁটাপথে এ রাজ্যের সীমানা। তার ওপারে গেলেই তো অন্য রাজ্য। আপনি নির্বাসনের দোরগোড়ায় পৌঁছেই গিয়েছেন। আপনি বলুন। আমরা শুনব”।ভল্লা ঘাড় ঘুরিয়ে প্রশ্নকর্তার দিকে তাকাল, দেখল তার পিছনে অন্ততঃ পনের জন যুবক দাঁড়িয়ে আছে, তাদের সঙ্গে আছে বেশ কিছু কিশোর ও বালক! ভল্লা ঘুরে বসল, যাতে দুপক্ষকেই দেখা যায়। তার বাঁদিকে পাথরের আসনে বসা প্রাজ্ঞজনেরা, আর ডানদিকে অর্বাচীন যুবক-কিশোরের দল। তার কাছে অর্বাচীন যুবক-কিশোররাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ – তাদের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ গড়ে তোলাই এখন তার একমাত্র লক্ষ্য।ভল্লা প্রাজ্ঞজনদের দিকে তাকিয়ে বলল, “আপনাদের অনুমোদন ছাড়া সব কথা প্রকাশ্যে আনা উচিৎ হবে কি?”যে বৃদ্ধ রাজশ্যালক সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন, তিনিই বললেন, “আমরা সত্য সংবাদ শুনতে চাই...তুমি বলো”।ভল্লা এবার যুবকদের দিকে তাকিয়ে বলল, “তোমরা কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে, ভাই? বসো না। নয়তো আমাকেই উঠে দাঁড়াতে হবে”। ভল্লার অনুরোধে সকলেই বসল। কৌতূহলী মুখে তারা তাকিয়ে রইল ভল্লার মুখের দিকে। ভল্লা বলল, “দেখুন, আমি নগররক্ষী বটি, কিন্তু বিশেষ নগররক্ষীদের মধ্যে একজন। এই বিশেষ ব্যাপারটি বুঝতে গেলে, রাজশ্যালকের চরিতামৃতকথাও জানতে হবে। আগে সেই কথাটিই সেরে নিই। দুর্গ প্রাকারের মধ্যেই রাজশ্যালকের নিজস্ব একটি মহল আছে। কিন্তু সে মহলে তিনি রাত্রিযাপন করেন না। কারণ তাঁর রাত্রিযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় যে বিপুল আয়োজন, তাতে দুর্গের প্রশাসনিক বিধিবিধান ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। অতএব দুর্গের বাইরে ক্রোশ দুয়েক দূরে, রাজপথের ধারেই তাঁর নিজস্ব একটি প্রমোদভবন নির্মিত হয়েছে। তা প্রায় বছর ছয়েক তো হতে চলল। এবং বলা বাহুল্য, সে প্রমোদভবন নির্মাণ হয়েছে মহামান্য রাজার অনুমোদনেই!সেই প্রমোদভবনের সম্মুখে আছে বিবিধ ফুল ও ফলের বিস্তৃত উদ্যান। বিচিত্র ফুলের প্রচুর লতাবিতান ও লীলাকুঞ্জ। বেশ কয়েকটি কৃত্রিম প্রস্রবণ। প্রমোদভবনে ঢোকার সিঁড়ির দুপাশে, অলিন্দে সাজানো আছে অজস্র নগ্নিকা মূর্তি। গৃহের অন্দরে কী আছে, জানি না, কারণ সেখানে আমাদের প্রবেশের অনুমতি নেই। ওই সমস্ত নগ্নিকা মূর্তির দুহাতে রাখা থাকে পেতলের দীপ। সন্ধ্যার পর সেই নগ্নিকা-মূর্তিদের করকমলের প্রতিটি দীপ যখন জ্বলে ওঠে সে প্রমোদভবনকে ঊর্বশী-রম্ভার নাচঘর মনে হয়। সুসজ্জিত সেই প্রমোদভবনে রাজশ্যালক প্রতিদিন সন্ধ্যায় যান। সারারাত্তির সুরা ও নারীতে ডুবে থাকেন। খুব সম্ভবতঃ সূর্যোদয়ের পর দেড় প্রহরে তাঁর ঘুম ভাঙে এবং মোটামুটি দ্বিপ্রহরে তাঁর নিজস্ব ঘোড়ার গাড়িতে দুর্গ প্রাকারের ভিতর নিজের মহলে ফিরে যান। এই হচ্ছে তাঁর প্রাত্যহিক কর্মকাণ্ড। শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা কোন ঋতুতেই তাঁর এই অভিসার যাত্রার কোন ব্যত্যয় হয় না – কারণ তাঁর কাছে সম্বৎসরে একটিই ঋতু – মধুর মধুঋতু! নিত্যনৈমিত্তিক একই ভোগে সুরসিক রাজশ্যালকের সন্তুষ্টি হয় না। তিনি সর্বদা নিত্য-নতুন রমণী সম্ভোগের কামনা করেন। এবং কুলবধূদের কুলনাশ করে তিনি যে আনন্দ পান, বারবধূ সম্ভোগ তার তুলনায় কিছুই নয়। অতএব যাওয়া-আসার পথে তাঁর তীক্ষ্ণ নজর থাকে, যে কোন যুবতী রমণী – সে সধবা কিংবা বিধবা। অধবা তরুণী কিংবা বালিকা। তাদের কেউ যদি সুন্দরী হয়, তবে রাজশ্যালকের গ্রাস থেকে সেই অভাগীদের পরিত্রাণের উপায় থাকে যৎসামান্য। মহানুভব রাজার এই বিষয়টি অগোচরে ছিল না। রাজশ্যালকের এই দুরাচারের প্রতিকার চিন্তা করে তিনি আমাদের মতো বিশেষ কিছু রক্ষীকে নিযুক্ত করলেন। আমাদের কাজ রাজশ্যালকের যাত্রাকালে, তাঁর যাত্রাপথে কোনভাবেই যেন কোন রমণী তাঁর দৃষ্টিপথে না আসে, সেদিকে লক্ষ্য রাখা। এক কথায় ওই সময়ে সকল রমণী যেন গৃহের ভিতরে থাকে। কেউ যেন কোনভাবেই রাজপথে, নিজ গৃহের সামনে প্রকাশ্যে না আসে”।সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে ভল্লা একটু বিরাম নিল, কিছুক্ষণ পর বলল, “মহানুভাব রাজা জেনেশুনেই এই ক্ষুধার্ত হায়নাকে রাজপথে অবারিত চলাচলের অনুমতি দিলেন। কিন্তু নিরীহ সাধারণ নগরবাসীকে পরামর্শ দিলেন ঘরের দরজায় খিল এঁটে থাক। আর আমাদের নির্দেশ দিলেন, সকলে দরজায় ঠিকঠাক খিল এঁটেছে কিনা সেদিকে নজর দিতে। স্বাধীন হায়নাটাকে জব্দ করার নির্দেশ তিনি দিতে পারলেন না!”কথা থামিয়ে হঠাৎই ভল্লা যেন শিউরে উঠল, বলল, “ছি ছি। রাজার অন্নে প্রতিপালিত হয়ে আমি রাজ-সমালোচনা করে ফেললাম? আমার কর্তব্য বিনা বিবেচনায় রাজার নির্দেশ পালন করা। সেখানে বিবেকের তো কোন স্থান নেই! এ আমি, এ আমি কী বলে ফেললাম? ছিঃ”। মাথা নীচু করে ভল্লা মাটির দিকে তাকিয়ে বসে রইল চুপ করে।উপস্থিত কেউই কোন কথা বলল না। সকলেই তাকিয়ে রইল ভল্লার দিকে। সকলেই যেন মনে মনে ভল্লার বক্তব্যের ভাল-মন্দ বিচার করে দেখছে। নির্বিচারে রাজাদেশ মান্য করাই উচিৎ নাকি কখনো কখনো বিবেকের নির্দেশকেও সমীহ করা বিধেয়?সেই বৃদ্ধ আবার বললেন, “তুমি বলো ভল্লা। আমরা জানি তোমার বিচার এবং দণ্ডবিধান হয়ে গেছে। তার পরিবর্তন আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তবু তুমি বলো, আমরা শুনব”। বৃদ্ধকে সমর্থন করে বেশ কিছু যুবক বলে উঠল, “হ্যাঁ, ভল্লাদা বলো”। ভল্লা মাথা তুলে সকলের মুখের দিকে তাকাল। তার মনে হল, যুবকদের মধ্যে কয়েকজনের চোখে যেন ক্রোধের স্ফুলিঙ্গ। ভল্লা বিলম্ব না করে বলল, “সেদিনের ঘটনার কথা আপনাদের আগেই বলেছি। বিবেকের তাড়নায় আমি ওই কাজ করেছিলাম। কিন্তু হত্যা তো করিনি, চরিত্রহীন লোকটার মনে ভয় ধরাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সর্বশক্তিমান মহানুভব রাজা কি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না, তাঁর ওই লম্পট শ্যালককে? লোকটা দিনের পর দিন অপরাধ করেও যে দিব্য স্ফূর্তিতে রয়েছে, সে কি রাজার প্রশ্রয়ে নয়? ওই গর্ভস্রাব লোকটি প্রত্যেক রাত্রে অজস্র অর্থের যে অপচয় করে চলেছে, সে অর্থ কি তার নিজের উপার্জিত নাকি রাজকোষের? অর্থ উপার্জনের মতো কোন যোগ্যতাই যে তার নেই – সে কথা আমরা সকলেই জানি। আপনাদের মতো লক্ষ লক্ষ প্রজার ঘাম-ঝরানো পরিশ্রমের শুল্ক থেকে ভরে ওঠা রাজকোষের অর্থ, কোন অধিকারে ওই লোকটি এভাবে অপচয় করে চলেছে সে প্রশ্ন আপনারা করবেন না?”বয়স্ক মানুষরা ভল্লার এই কথায় চমকে উঠলেন। জনৈক বৃদ্ধ বললেন, “উত্তেজনার বশে এ সব বলা তোমার সমীচীন নয় ভল্লা। তুমি রাজার বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলছ? সরাসরি আমাদের রাজাকেই তুমি অভিযুক্ত করছ? এ তো বিদ্রোহের কথা?”“কিন্তু প্রশ্নগুলো তো অবান্তর নয়, জ্যাঠামশাই” যুবকদের মধ্যে জনৈক উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল, “ভল্লাদা, তুমি জান না, আমাদের এই রুক্ষ বৃষ্টি-বঞ্চিত অঞ্চলে আমরা কী কঠোর পরিশ্রম করি এবং কত সামান্য ফসল ঘরে তুলতে পারি। সেই ফসলেরও রাজকর দিতে হয় এক-তৃতীয়াংশ! সারা বছর আমরা কী খাব, কী পরব। সে কথা রাজা তো চিন্তা করেন না। আর তাঁর শালা রাজধানীতে বসে নিত্য মোচ্ছব চালিয়ে যাচ্ছে?”বয়স্ক মানুষরা শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। কথায় কথায় ছেলে ছোকরার দল উত্তেজিত হয়ে উঠছে। এরপর আর সামলানো যাবে না। এসব আলোচনার কথা রাজকর্মচারীদের কানে গেলে অশান্তি শুরু হবে। এই প্রসঙ্গ এখনই বন্ধ হওয়া দরকার। সেই বৃদ্ধ মানুষটি আচমকা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, “কথায় কথায় অনেক বেলা হয়ে গেল হে, চলো বাড়ি যাওয়া যাক – স্নান খাওয়া সারতে অবেলা হয়ে যাবে”।ভল্লাও উঠে দাঁড়াল। সকলকে নত হয়ে প্রণাম করে বলল, “হ্যাঁ তাইতো, বেলা অনেক হল। আর দেরি হলে ওদিকে কমলি-মা আমার পিঠ ফাটাবে। ছোটমুখে অন্যায্য কিছু কথা যদি বলে ফেলে থাকি, ক্ষমাঘেন্না করে নেবেন”।ভল্লা গ্রামের ছোকরাদের আচরণে আশ্বস্ত হল। নিশ্চিন্ত হল। ছেলেগুলো একেবারে মিয়োনো নয়, ভেতরে আগুন আছে। ভল্লা তাড়াহুড়ো করবে না, ধৈর্য ধরে সে আগুনকে উস্কে নিতে পারবে। উত্তেজিত যুবকটির চোখে চোখ রেখে সে কিছুক্ষণ দাঁড়াল, তারপর একটু চাপা স্বরে বলল, “বাড়ি যাও ভাইয়েরা, পরে আরও কথা হবে”।ক্রমশ...রাবণের প্রার্থনা - তাতিন | ছবি : DALLE - 3 এই তো বাবু হয়ে বসেছি দক্ষিণেবন্ডদাতার আজ শূন্য হাতধ্বংস করে দাও এদেশ যদি চাওআমার মালিকেরা সুখেতে থাককোথায় গেল আজ সূর্যতিলক আরকোথায় ফার বনে মরেছে কাকনবমীমিছিলের অস্ত্র ঝনঝনেপকেটে গেল না কি পনেরো লাখ?বাজাও রাষ্ট্রের চাষির ঘরে ঘরেবিরাটপুঁজিদের ঋণের ঢাকএবং বিরোধীর সকাশে অহরহএজেন্সিরাও আসতে থাকআমারই পাতে এত দিয়েছ মাশরুমঅজীর্ণতে কেন ভুগব আরচৌকিদার করো আবার ঈশ্বরআমার মালিকেরা লাভেতে ফাঁক।কাদামাটির হাফলাইফ - ইট পাথরের জীবন - ইমানুল হক | নামাঙ্কনঃ ইমানুল হক। ছবিঃ র২হকথা - ২৯মায়েরা মুঠো করে চাল রেখে দিতেন আলাদা জালা/ কলসি বা বড় হাঁড়িতে। হিন্দু মুসলমান সব বাড়িতেই ছিল এই রীতি।দীনদুঃখীদের সাহায্য দেওয়া হতো।পোশাক আসাক। মেয়ের বিয়ে হয়ে গেলেই সাদা শাড়ি। সেটা সাধারণত ৩২-৩৩ বছরেই হতো।বিধবা হলে একটু আলাদা। হিন্দু হলে সাদা ধুতি। মুসলিম মেয়েরা সবাই সাদা শাড়ি পরতেন না।হিন্দু বিধবা মাছ মাংস ডিম পেঁয়াজ রসুন খেতে পারবেন না।মুসলিম মহিলা সব খেতে পাবেন।আবার বিয়ে করতেও পারবেন।আমার গ্রামেই এমন বিয়ে দেখেছি।তবে মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েরা বিয়ে করতেন না।ভদ্রলোক হয়ে গেছেন যে!বর্ধমান শহরে একজন কলেজের দিদির বিয়ে হতে দেখেছি, স্বামীর মৃত্যুর পর।তাঁর স্বামী বিয়ের অল্পদিন পরেই খুন হয়ে গিয়েছিলেন।বাংলাদেশের মনীষা ব্যক্তিত্ব বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খানের স্ত্রী হেলেনা খান একটা প্রশ্ন করেছিলেন, তোমাদের এখানে এত কুঁজো হয়ে হাঁটা বয়স্ক মহিলা দেখি কেন?ঢাকায় দেখেন না?না, তেমন দেখিনি।কথাটা শোনার পর আমার মনে হয়েছিল, এমনিতেই বেশিরভাগ বাড়িতে মহিলারা খাবারের বিষয়ে বঞ্চনার শিকার। তার ওপর বিধবাদের খাওয়া দাওয়ার উপর প্রচুর বিধিনিষেধ। মাছ ডিম মাংস -- আমিষ জাতীয় খাবার খাওয়া নিষেধ। এর একটা কারণ হতে পারে।আরেকটা ঘটনা মনে পড়ল। ১৯৯৮। গুজরাট যাচ্ছি লোকসভা নির্বাচনের খবর সংগ্রহে। ট্রেনে এক গুজরাটি ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হল। তিনি বাঙালির ইংরেজি শিক্ষার খুব প্রশংসা করলেন। তারপর বললেন, আপনাদের বাঙালিদের ভাবা উচিত কাশী মথুরা বৃন্দাবনে এত বাঙালি বিধবা কেন?এটা তো একটা জাতির লজ্জা। কীভাবে কষ্ট করে ওঁদের বেঁচে থাকতে হয়, খোঁজ নিয়েছেন কখনও?আমি নিরুত্তর।আমার নিজের ধারণা, বাংলায় এত খাদ্য বৈচিত্র্যের পিছনে আছে বিধবাদের অবদান।রান্নাবান্নার দায়িত্ব তাঁদের কাঁধে। খাদ্যাখাদ্যের কঠিন বাছবিচার।তাঁরাই নানাবিধ নিরামিষ মুখরোচক খাবারের স্রষ্টা।আলুর খোসা, লাউয়ের খোসা, কুমড়োর খোসা দিয়েও কীসব চমৎকার রান্না করেছেন।এবং এর ফলে একটা ক্ষতিকর দিকও আছে। প্রচুর তেলের ব্যবহার।আমার দাদার এক বন্ধু ছিলেন বাসুদেব পণ্ডিত। প্রধান শিক্ষক হিসেবে অবসর নিয়েছেন। তিনি ১৯৭৯তে নুরপুর ক্যানেলের ধার দিয়ে হেঁটে আসার সময় একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেন, সেটা আজ মনে পড়ছে।তাঁর কথা, তোদের (মুসলমানদের) রান্না এত ভালো কেন জানিস?আমি চুপ।বললেন, তোদের রান্না সেজে রান্না। ভাজাভুজি কম। সব সব্জি একসঙ্গে চাপিয়ে দিয়ে একটু তেলে নেড়ে নিয়েই জল দিয়ে সেদ্ধ। খালি মাংসতেই যা একটু তেলঝাল।পরে কথাটা খেয়াল করেছি।আমাদের বাড়িতে মাছ ভাজা খেলে আলাদা বিষয়। না হলে মাছ ইলিশের মতোই না ভেজে রান্না করা হতো। এবং তার স্বাদ ছিল অসাধারণ।আমি নিজে রান্না করলে মায়ের পদ্ধতিতেই করি। মা সরাসরি মাছ দিতেন। আমি একটু সাঁতলে নিই।রান্না পদ্ধতির এই তফাৎটুকু বাদ দিলে খাদ্যাভ্যাস পোশাক রীতি সব এক।আরও দুটো তফাৎ আছে। আমার আবার বেনেপাড়ায় জগন্নাথ দত্তের মায়ের পাঁচফোড়ন দিয়ে ছ্যাঁকছোঁক করে আলু বাঁধাকপি রান্নার গন্ধটা দারুণ লাগতো। শীতকালে আমি বেলা এগারোটা নাগাদ বেনেপাড়া যেতাম ওই গন্ধের ঝোঁকে।কোনদিন কথাটা বলা হয়ে ওঠেনি। ফলে খাওয়াও হয়নি।কিন্তু গন্ধ নাকে লেগে আছে।আরেকটি তফাৎ দেখেছিলাম।পরোটার বিষয়ে। মুসলিম বাড়ির পরোটা বড় গোল। বেশ মোটা। পারলে ১০০ গ্রামে একটা পরোটা বানিয়ে ফেলবে। তার আবার পরত ছাড়বে মাখামাখির গুণে। ১৯৭৭ -এ ধারান গ্রামে ফুটবল খেলা দেখতে গিয়ে আমার পত্রবন্ধু দীনবন্ধু দাসের বাড়িতে রাতে থেকে গেলাম। ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ি। সন্ধ্যায় পরোটা খেতে দিলেন কাকিমা। তেকোনা। এবং আলু কালোজিরার পাতলা তরকারি। পরোটা পছন্দ হলো না। কিন্তু তরকারিটির প্রেমে আজও পড়ে আছি।মুসলিম বাড়িতে পরোটার সঙ্গে আলু ভাজা দেওয়া ছিল রীতি। সঙ্গে চিনির সিরা। পারলে ডিমের ভুজিয়া।গ্রামে ধর্ম কর্মে খুব মতি ছিল না।বাঙালি জীবন যেমন হয় আর কী!কথায় কথায় আল্লার কিরে (দিব্যি), মা কালীর দিব্যি খুব চালু ছিল বটে-- কিন্তু ১৯৭৮ এ মসজিদে নামাজ পড়তে যেতেন নিয়মিত চার পাঁচজন।২০০৪ এ সংখ্যাটি দাঁড়ায় ১৮ জন।এখন প্রায় ১০০ জন।জনসংখ্যা আড়াই হাজারের বেশি।সত্তর দশক থেকেই তাবলিগ জামায়াতের আনাগোনা। আশির দশকে শুক্রবার শুক্রবার শুরু হল, বাড়ি বাড়ি ঘুরে নামাজের দাওয়াত দেওয়া।তবে গ্রামে বছরে একবার জলসা হতো।সে বহুদিন আগে থেকেই।তবে সব বছর হতো না।কারণ অনেক পয়সা কড়ির ব্যাপার। ইসলামি জলসার বক্তাদের টাকা দিতে হতো বক্তৃতা করাতে। পূজারীদের যেমন পূজার মন্ত্র পড়ার জন্য টাকা দিতে হয়। এছাড়া রাতে সবার খাওয়ার ব্যবস্থা হতো।একবার মাংসের খিচুড়ি তথা তেহারি খেয়েছিলাম। এখনও মুখে লেগে আছে। শুক্রবার মসজিদে নামাজের পর বাচ্চারা গেলে ক্ষীর বা পায়েস পাওয়া যেত। ৬৫ ঘর মুসলমান ছিলেন গ্রামে। কেউ না কেউ কারও নামে বা কল্যাণকামনায় ক্ষীর বা পায়েস রেঁধে পাঠাতেন। নামাজি শুক্রবার বড়জোর ১০ জন।আর আমরা বাইরে বসে থাকা ক্ষীরের অপেক্ষায় অন্তত ২০-২৫ জন।ছোটরা কেউ নামাজ পড়তেন না। কেউ জোর করতোও না।ক্ষীর খাওয়ার দলে হিন্দু মুসলমান সব বাচ্চারাই থাকতেন।ওলাইচণ্ডী পূজার প্রসাদ তো হিন্দু মুসলমান সবাই খেতেন। সরস্বতী পূজার প্রসাদ তো বলাই বাহুল্য।সরস্বতী পূজার পাণ্ডা তো গ্রামের মুসলমান ছেলে-মেয়েরাই। তাঁরাই তো বিদ্যালয়ের ৯০%।শিক্ষক একজন মুসলমান। তাতে কী?আমি যে হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় পূজার রীতিনীতি অনেকেরই চেয়ে বেশি জানি, তার একটা বড় কারণ আমার গ্রাম।এখন কিছুটা বদলেছে ভিতরে ভিতরে। তবে একটা নতুন সংযোজন হয়েছে, তৃণমূল জমানায় মাঘ মাসের ওলাইচণ্ডী পূজার মেলার শেষ দিনে একসঙ্গে বসে খিচুড়ি খাওয়া।আর কয়েকটা পরিবর্তন হয়েছে। ফুটবল খেলার মাঠে লোক নেই। সেখানে কিছুটা ঘিরে ঈদগাহ তলা। বেনে পাড়া বামুনপাড়ায় খেলার জায়গা ছিল না। দুটি পরিবার হাওড়া প্রবাসী হওয়ায় জায়গা মেলে। ছোটখাটো খেলার মাঠ হতেই পারতো। সেখানে এখন বড় দুর্গামন্দির। শিবমন্দির ছিল আগে মাটির। এখন শিব আর ওলাইচণ্ডীর আলাদা ঘর হয়েছে। আগে দুর্গাও ওখানে আসতেন। শিব লিঙ্গ সারা বছর থাকে। ওলাইচণ্ডীর বিসর্জন হয়। দুর্গারও। তবু আলাদা দুটি মন্দির।খেলার জায়গা নেই। গোলাম হল ছিল ২০০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত খেলার জায়গা। বিক্রি হয়ে গেছে। এখন সেখানে কয়েকটি বাড়ি। সবে বরাত আর কালীপুজোর সময় মোমবাতি জ্বালানো, ধূপ জ্বালানো ছিল। আছে। বোম ফাটতো, তারা বাজি হতো। হয়। তবে সবে বরাত বা বিজয়ায় বাড়ি হিন্দু মুসলমান বন্ধুর দল মিলে খাবার বা নাড়ু সংগ্রহ বন্ধ। ইদ বকরিদে বাড়ি বাড়ি ঘুরে বড়দের সালাম করা কমেছে। বিজয়া দশমীতেও তাই। নতুন বউ এলে পীরতলা বা বারোয়ারি তলায় এসে একবার থামতো। কমে গেছে। প্রায় নেই। ধর্ম বেড়েছে। লোকাচার কমেছে। বিয়েতে হিন্দু মুসলমান একসঙ্গে বসে খাচ্ছে। জাতপাত অস্পৃশ্যতা প্রায় নেই। কিন্তু একটা বিদ্বেষী আবহাওয়া তৈরির চেষ্টা হচ্ছে। দু'পক্ষের কিছু লোক অপচেষ্ট।গ্রামে অদ্ভুত বিষয়, রাজনৈতিক ঝামেলা আছে। ১৯৭০ -৭৫ রাজনৈতিক হিংসা ছিল। ২০০৯ থেকে ২০১৯ আবার তা অল্প হলেও দেখা দেয়।কিন্তু শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ। কিন্তু মারদাঙ্গা নেই।আর সাম্প্রদায়িক ঝামেলা এখনও আমাদের তিনটি গ্রামে হয়নি।এই ঐতিহ্য চিরবহমান থাকুক।(ক্রমশঃ)
হরিদাস পালেরা...
স্মৃতির রাজ্য শুধুই শ্লোগানময়-২ - প্রবুদ্ধ বাগচী | স্মৃতির রাজ্য শুধুই শ্লোগানময়-২প্রবুদ্ধ বাগচী আশির দশকের একেবারে শেষপর্বে এসে রাজ্যের ও দেশের রাজনীতির ইস্যুগুলোই পাল্টে যায়। বোফর্স কামান কেনার সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী রাজীবের নাম যুক্ত হয়ে যাওয়া যদি একটা পর্ব হয় তবে আরেকটা প্রান্ত হল মণ্ডল কমিশনের রিপোর্টকে কেন্দ্র করে দেশে দলিত ও পিছড়েবর্গ জনগোষ্ঠীকে নিয়ে নতুন এক ভোট রাজনীতি। দুটো বিষয়ই সামনে এনে সেই সময় মিডিয়ার নজর কেড়ে নিয়েছিলেন রাজীব মন্ত্রীসভার প্রতিরক্ষামন্ত্রী মণ্ডার রাজা বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং ওরফে ভিপি। কার্যত “পিছড়েবর্গ” এই শব্দটা তখন দেশের রাজনীতিতে নতুন পরিভাষা হিসেবে উঠে এল। আরও দুটো বিষয় এখানে বলতে হবে। একটা হল এই মণ্ডল রাজনীতি-র মূল কেন্দ্র ছিল দেশের তফশিলী জাতি ও পিছিয়ে পড়া শ্রেণি যারা উচ্চবর্ণের হিন্দুজনগোষ্ঠীর বাইরের মানুষ। এই শ্রেণির দ্রুত মূল রাজনীতির স্রোতে উঠে আসা উচ্চবর্ণের হিন্দুদের দল হিসেবে ভারতীয় জনতা পার্টি সুনজরে দেখেনি। প্রধানত হিন্দি বলয়ে নিজেদের ভোটব্যাঙ্ক রক্ষার জন্য তাঁরা সরাসরি এই মণ্ডল রাজনীতির বিরোধিতা করে সংরক্ষণ-বিরোধী অবস্থান নিলেন —- খবরের কাগজের ভাষায় এর নাম হল ‘কমণ্ডলু’ রাজনীতি, যার প্রধান প্রবক্তা ছিলেন লালকৃষ্ণ আদবানি ও তার কিছু বাছাই সহযোগী যাদের আর দু-তিন বছরের মধ্যেই আমরা দেখতে পাব আরও আরও হিংস্র ভূমিকায়। এদের উস্কানিতে কিছু বর্ণহিন্দু ছাত্র নিজেদের গায়ে আগুন দিয়ে বিষয়টাকে আরও তীব্রতর করে। তবে সবথেকে কুৎসিত ও অপমানজনক ঘটনা হল এদেরই ছাত্রযুব সংগঠনের কর্মীরা পিছিয়ে পড়া মানুষকে সংরক্ষণের আওতায় আনার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য রাস্তায় জুতো পালিশ ও জুতো সারাই করতে বসে যান চর্মকার-সম্প্রদায়কে বিদ্রূপ করে। আজকে সারাদেশেই যখন পিছিয়ে পড়া জাতির মানুষকে সামাজিক শারীরিক ও আর্থিক হিংসার শিকার হতে দেখি আমরা তখন হয়তো মিলিয়ে নেওয়া যায় আসলে তার শিকড় কোন গভীরে ঢুকে বসে আছে। রাজ্যের রাজনীতিতে এই মন্ডল-প্রসঙ্গ ততটা উচ্চকিত হতে পারেনি কারণ বামফ্রন্টের আমলে মনে করা হত এরাজ্যে জাতের বিচার তেমন কিছু একটা বিষয় নয়, এখানে শ্রেণির অবস্থানই প্রধান। কিন্তু ‘কমণ্ডলু’র রাজনীতি যে একটা দুর্যোগের আশঙ্কা ডেকে আনছে এটা কুশলী বামনেতৃত্ব কেউ কেউ বুঝেছিলেন। তা নিয়ে কিছু দেওয়াল লিখন যে হয়নি তা নয় । তাদের আহ্বান ছিল, ‘বিজেপির সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে পরাস্ত করুন’ এই ধরনের —-- নিজেদের আদর্শগত কাজ কেন তাঁরা জনগণের ওপর চাপিয়ে দিতে চাইছিলেন তা অবশ্য খুব স্পষ্ট ছিল না। বরং তাদের সামনে অন্য একটা ঘোর বিপর্যয় এসে পড়ল সোভিয়েতের পতন ও তার প্রতিক্রিয়ায় তথাকথিত সোস্যালিস্ট ব্লক ছন্নছাড়া হয়ে যাওয়ার মধ্যে দিয়ে। ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয়, দেশের ও রাজ্যের তাবড় তাবড় বাম তাত্ত্বিক নেতারা ওই দেশগুলির ভিতরের প্রকৃত ‘খবর’ রাখতেন না। দলীয় সফরে সোভিয়েট বা অন্য দেশে এঁরা অনেকেই গেছেন কিন্তু যেহেতু তাদের অনেকটাই ‘সাজানো বাগান’ দেখানো হয়েছিল তাই অন্দরের বার্তা তাঁরা পড়তে পারেননি। এই কথাটা বলছি আরও এই কারণে, এই সময়েই কিন্তু আমরা শহরের নানা জায়গায় দেওয়ালের লিখন দেখেছি — ‘মার্কসবাদ সত্য কারণ এটি একটি বিজ্ঞান’ বা ‘পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ সমাজতন্ত্র, সমাজতন্ত্রই শেষ কথা’ ইত্যাদি ইত্যাদি। এটা ঠিক, সোভিয়েতের ‘পতন’ হওয়ার সঙ্গে মার্কসবাদ ‘অসত্য’ প্রতিপন্ন হওয়ার কোনো সংযোগ নেই। কিন্তু পূর্ব ইউরোপের একেকটি দেশের করুণ বিপর্যয় দেখে বামমহলে একটু আড়ষ্ট কানাকানিও চলছিল —- আসলে ওই দেশগুলিতে বোধহয় প্রকৃত অর্থে সোশ্যালিজম ছিল না ! তাহলে তাঁরা দুনিয়ার তিনভাগের একভাগ ‘সমাজতন্ত্রের দখলে’ বলে দেওয়াল লিখেছিলেন কেন, এর জবাব তাঁরাই দিতে পারেন। কথায় বলে বিপদ কখনো একা আসে না। রাজ্যের তথা দেশের বামপন্থীদের সামনে ঠিক এর পরের দশকের গোড়াতেই মুখোমুখি হতে হল, দুটো নির্দিষ্ট বিষয়ে যার জন্য তাঁরা কতটা প্রস্তুত ছিলেন জানা নেই। শরিক দলগুলির নিজেদের অন্তঃকলহে কেন্দ্রের স্বল্পস্থায়ী জোট সরকারের পতন প্রায় অনিবার্য ছিল, ভিপি সিং সরকারের ওপর যে বিজেপি সমর্থন তুলে নেবে সামগ্রিক পরিস্থিতি সেদিকেই ইঙ্গিত করছিল, ঘটলও তাই। এর পরে লোকসভা নির্বাচনের মধ্যেই ঘটে গেল রাজীব গান্ধির মর্মান্তিক হত্যাকান্ড। সেই নির্বাচনে কংগ্রেস দল স্থায়ী সরকারের সমর্থনে প্রচুর দেওয়াল লিখেছিলেন — ‘কেন্দ্রে স্থায়ী সরকার গড়তে কংগ্রেসকে ভোট দিন’, দেওয়ালে নতুন এক শব্দের জন্ম দেখলাম আমরা — ‘খিচুড়ি সরকার’ । তাঁরা রাজীবজির ফিরে আসা ও নতুন সরকার গড়ার স্বপ্নও দেখিয়েছিল —-- হায়, তাঁরা জানতেন না অমন তরতাজা মানুষটা কীভাবে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবেন মানববোমার আঘাতে। জনগণেশের ইচ্ছেয় সেবার অবশ্য প্রধানমন্ত্রী পিভি নরসিনহা রাওয়ের নেতৃত্বে সরকার গড়লেন কংগ্রেস দল, তবে নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতার জন্য বাইরের কিছু সমর্থন অবশ্য দরকার হয়েছিল। তখন দেশে উঠে আসছে নতুন বিরোধী শক্তি ভাজপা, বাবরের নামাঙ্কিত মসজিদের জায়গাতেই তাঁরা নতুন রামমন্দির তৈরি করার নামে উত্তেজনা বাড়াচ্ছে দেশের। আর একই সঙ্গে দেশের নতুন অর্থমন্ত্রী হিসেবে মনমোহন সিনহা ঠিক সেই সময়েই দেশের অর্থনীতিকে ভাসিয়ে দিলেন খোলা হাওয়ায়। সাবেকি পরিকল্পিত অর্থনীতির ‘নেহেরু মডেল’ সেই প্রথম ধ্বস্ত হল এক শিখ প্রৌঢ়ের হাতে। এ এমন সর্বনেশে হাওয়া যা আমূল বদলে দিতে লাগল এতদিনের চেনা অবয়ব। রাজ্যের দেওয়ালে দেওয়ালে গর্জে উঠলেন বামপন্থীরা। নতুন স্লোগান এল ‘খোলা বাজারি অর্থনীতি মানছি না, মানব না’, বলা হল ‘সরকারি ক্ষেত্রে ঢালাও বেসরকারিকরণ রুখতে হবে’, ‘লাভজনক সরকারি সংস্থার হস্তান্তর চলবে না’ ইত্যাদি ইত্যাদি। এই প্রতিটি দাবিই ছিল ন্যায্য, কিন্তু রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার তখন কেন্দ্রের শরিক নন ফলে সরকারি নীতিকে প্রভাবিত করার মতো অবস্থায় তাঁরা ছিলেন না। অন্যদিকে ধীরে ধীরে বাম- রাজনীতির পাশে পাশে ইতিউতি দেখা যেতে লাগল ‘কমল’ চিহ্নের পায়চারি। সম্ভবত, আদবানি ‘রাম-রথ’ তৈরি করে দেশ পরিভ্রমণে বেরোলেন এর কাছাকাছি সময়েই। ইতিমধ্যে বিজেপি উত্তরপ্রদেশের বিধানসভায় ক্ষমতা দখল করে ফেলেছে। ‘রাম রাজনীতির’ হাত ধরে উঠে এল কিছু নতুন শব্দ আর স্লোগান —- ‘রাম-শিলা’, ‘ করসেবা’ এবং খুব ব্যঞ্জনাবহ ‘সিউডো সেকিউলার’ বা ‘মেকি ধর্মনিরপেক্ষ’ এবং ‘সংখ্যালঘু তোষণ’ । দেওয়ালের দখল তাঁরা যে খুব একটা নিতে পেরেছিলেন এমন নয় তবে ‘মন্দির ওহি বানায়ঙ্গে’র মতো হিন্দিভাষী স্লোগান সেই প্রথম ঢুকে পড়ল বাংলা বাজারে পরে যাকে আরো স্তরে স্তরে বিকশিত হতে দেখব আমরা। একই সঙ্গে ‘বেআইনি অনুপ্রবেশকারী’ নামক এক শব্দও খুব কায়দা করে ভাসিয়ে দেওয়া হল দেশভাগের প্রত্যক্ষ শিকার এই রাজ্যে। বামপন্থীরা যে নীরব ছিলেন তা নয়। তাঁরা আওয়াজ তুলছিলেন ‘সাম্প্রদায়িক বিজেপি বাংলা থেকে দূর হঠো’ বা কবি সুকান্তের কবিতাংশ ‘বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটি/ বুঝে নিক দুর্বৃত্ত’। এই সময় কার্যত দুটো ফ্রন্টেই লড়ার চেষ্টা করছিলেন তাঁরা — নতুন অর্থনৈতিক নীতি নিয়ে একদিকে কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁদের বিরোধ অন্যদিকে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বাড়বাড়ন্ত —- তখন তাঁরা দুই পক্ষ থেকেই সমদূরত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন। কেন্দ্রীয় ‘সর্বনাশা’ আর্থিক নীতির বিরুদ্ধে তাঁরা কত যে বনধ ডেকেছেন তা আর বলার নয় —- এইসব হরতালের পক্ষে প্রচারে ছিল কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী মনমোহন সিনহার আদ্যশ্রাদ্ধ। তাঁরা একরকম নামই দিয়েছিলেন ‘মনমোহিনী অর্থনীতি’, তাঁকে ‘বিশ্বব্যাঙ্কের দালাল’, ‘মার্কিন পুঁজির চৌকিদার’ ইত্যাদি নামেও ডাকা হয়েছে বারবার, এমনকি নিজেদের স্বার্থেই আই এম এফ যে তাঁকে দেশের অর্থমন্ত্রী করেছেন এই অপবাদও দেওয়া হয়েছে। এগুলির সত্যাসত্য বিচার করার কোনো পরিসর এখানে নেই। কিন্তু এইসবের মধ্যেই আদবানির ‘রামরথ’ এসে পড়ল রাজ্যের সীমানায়। প্রচারমাধ্যমের বিপুল আলো এবং দাঙ্গার উস্কানির সামনে কিছু স্লোগান তৈরি হল উভয়পক্ষেরই। স্বভাবত ভাজপার স্লোগানে ছিল উগ্র ঝাঁঝ —- ‘এক ধাক্কা আউর দো/ উস ধাঁচা কো তোড় দো’ র আড়ালে ছিল বাবরের নামাঙ্কিত মসজিদ ভেঙে ফেলার প্ররোচনা। রাজ্যের বামফ্রন্ট সম্প্রীতি ও ধর্মনিরপেক্ষতার আহ্বানে দেওয়াল লিখলেন, স্লোগান দিলেন, মিছিল করলেন, তৈরি করলেন মানববন্ধন। তবে আদবানির রথ-কে, যাকে ডাকা হত ‘দাঙ্গা রথ’ বলে, কিন্তু এই রাজ্যে ঠেকানো গেল না —-- তিনি গড়িয়াহাটার মোড় দিয়ে রথ নিয়ে সভা করতে করতে এগোলেন আসানসোল পেরিয়ে বিহারের দিকে। আর পিছড়েবর্গের প্রতিনিধি হিসেবে যে লালুপ্রসাদ যাদব কে উচ্চবর্ণ ‘লালু লালু’ বলে ব্যঙ্গ করত, বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে রাজনৈতিক ঝুঁকি নিয়েও সেই তিনিই আদবানির রথ আটকে তাঁকে বন্দি করে পাঠিয়ে দিলেন সরকারি অতিথিশালায়। এটা সেই সময়ের প্রেক্ষিতে একটা বড় রাজনৈতিক ইভেন্ট। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবাবু মনে করেছিলেন রথ আটকালে বিজেপি বেশি প্রচার পেয়ে আরও গোলমাল করবে, সত্যিই তেমন কোনো বড় সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ রাজ্যে হয়নি, তার কৃতিত্ব নিশ্চয়ই বামপন্থীদের প্রাপ্য। তবে এখানে এটাও বলা দরকার, এর পরের পর্বে যখন ‘রামমন্দির আন্দোলন’ আরও তুঙ্গে উঠল তখন কিন্তু রাজ্যের উদ্বাস্তু জনগোষ্ঠীর একটা অংশ তাদের এতদিনের বামপন্থী অবস্থান পরিবর্তন করে কিছুটা হলেও ‘রামপন্থী’দের দিকে হাত বাড়িয়েছিল। এটা দেখা গেল যখন ‘রামশিলা’ নামক ইট নিয়ে দলে দলে মানুষ ছুটলেন অযোধ্যায়। এই ‘করসেবা’র আহ্বানে কিছু দেওয়াল লেখাও চোখে এসেছিল সেই সময়। অবশেষে, বিরানব্বই এর ডিসেম্বরে ভারতের ইতিহাসের সব থেকে কলঙ্কিত অধ্যায়টির সূচনা হল পাঁচশো বছরের পুরোন মসজিদ ভেঙে ফেলার মধ্যে দিয়ে। দেশের প্রধানমন্ত্রী পিভি নরসিমহা রাও রইলেন নীরব দর্শক আর উত্তরপ্রদেশের নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী কল্যাণ সিং নিজে দাঁড়িয়ে থেকে এই ধ্বংসলীলায় উৎসাহ দিলেন —- একই ছবির ফ্রেমে দেখা গেল আদবানি, মুরলি মনোহর জোশি, উমা ভারতী প্রমুখ উগ্রবাদী ষড়যন্ত্রীদের। এই আগুন নিয়ে খেলার পরেই ঘোষিত হল তাদের নতুন স্লোগান : ইহে তো কেবল ঝাঁকি হ্যায়/ কাশি মথুরা বাকি হ্যায়। এই অসম্ভব এক উত্তেজনার মুহূর্তে কলকাতা শহরেও যখন ফুলকি ছড়াচ্ছে আগুনের, রাজধানীতে শুরু হয়েছে সেনার রুট মার্চ — ঠিক তখনই উঠে এসেছিল কিছু নিজস্ব স্লোগান। বামপন্থীরা সেই সঙ্কট মুহূর্তে হয়তো দেওয়াল লেখেননি কিন্তু স্লোগান তুলেছিলেন : ‘মানুষ আগে ধর্ম পরে / ধর্ম কেন মানুষ মারে ?’ —- বাস্তবিকই সারাদেশ তখন জতুগৃহ যার আগুনে লাশ গুণে গুণে ক্ষমতা দখলের স্বপ্ন দেখছেন হিন্দুত্ববাদীরা। এই সময়েই জনপ্রিয় ও প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে রাজনৈতিক কর্মী ও কবি সজল রায়চৌধুরীর একটি গানের কিছু অংশ : ‘হাতে হাত রেখে পার হব এই বিষের বিষাদসিন্ধু/ দুশমনদের ফাঁদে কেন বলো পড়ব’। এরই পাশাপাশি লালনের সুবিখ্যাত গান ‘সব লোকে কয় লালন কী জাত, সংসারে/ লালন বলে, জেতের কী রূপ দেখলেম না এই নজরে’ বা রবীন্দ্রনাথের পরিচিত কবিতার লাইন ‘ধর্মের বেশে মোহ এসে যারে ধরে/ অন্ধ সে জন মারে আর শুধু মরে’ সংহতির মিছিলে নতুন করে প্রাসঙ্গিক হতে থাকে। এইটাই বোধহয় বাঙালির সাংস্কৃতিক সৌন্দর্য যে জাতির কঠিন সময়ে কান্ডারী হয়ে এগিয়ে আসে আমাদের কবিতা গান নাটক ছবির সুমহান ঐতিহ্য। আজও যারা বাংলার বুকে মন্দির-মসজিদ আর হিন্দু-মুসলমান করছেন তাদের নিরেট মগজে এই সত্যিটা যদি একবারও প্রতিফলিত হত ! স্থায়ী সরকারের ধুয়ো তুলে কংগ্রেস কেন্দ্রের ক্ষমতায় এলেও তাঁদের প্রধানমন্ত্রী পিভি নরসিমহা রাও ছিলেন ভীরু ও দুর্বলচিত্ত। ফলে নব্বই দশকের মাঝামাঝি যে নির্বাচন হল তাতে খুব স্পষ্ট রায় তাঁদের পক্ষে গেল না। আবার সেই মিলিজুলি সরকারের হাতে চলে গেল দেশ। প্রধানমন্ত্রীর পদ নিয়ে রেষারেষি এল প্রকাশ্যে, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবাবুর কাছে প্রধানমন্ত্রীত্বের প্রস্তাব এল এবং তিনি প্রত্যাখ্যান করলেন। বামফ্রন্টের সঙ্গে তখনও কংগ্রেসের সম্পর্ক আদায় কাঁচকলায় ফলে রাজ্যের ভোটে সেবারও হই হই করে জিতে গেল বামেরা। কিন্তু এই ডামাডোলের বাজারে আসলে গোকুলে বেড়ে উঠছিল বিজেপি আর পোক্তভাবে কেন্দ্রের সরকারে আসতে গেলে যে কিছু ‘বন্ধুদল’ জুটিয়ে নেওয়া দরকার সেটাও তাঁরা বুঝেছিলেন। বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বর্ণহিন্দু জাতীয়তাবাদ নিয়ে কলকে পাওয়া যাবে না। তাই তৈরি হল এন ডি এ — যার মুখ হলেন তুলনায় ‘নরম হিন্দু’ বাজপেয়ি আর শরীর হলেন উগ্রহিন্দুত্বের ‘পোস্টারবয়’ আদবানি। দেশের রাজনীতি ধীরে ধীরে সরে আসতে লাগল একটা অন্যমেরুতে , রাজ্যের পরিস্থিতিও তার ব্যতিক্রম ছিল না। নিজের তীব্র ‘বাম-বিরোধী’ ইমেজ নিয়ে রাজ্য কংগ্রেসের সঙ্গে এতদিন তীব্র সংঘাতের মধ্যে দিয়ে যিনি চলছিলেন সেই যুব নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেস ছেড়ে বেরিয়ে এসে গঠন করলেন তৃণমূল কংগ্রেস। নব্বই সালের আগস্ট মাসে ভবানীপুর থানার সামনে তার শারীরিক নিগ্রহ ঘটিয়ে বামেদের অতি উগ্র সমর্থকরা মমতার পালে হাওয়া লাগিয়ে দিয়েছিলেন, তার বছর পাঁচের মধ্যে রাজ্যের নানা জায়গায় তার মেঠো আন্দোলন এবং কংগ্রেস হাইকম্যান্ড বা প্রদেশ কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর বিবাদ ছিল খবরের কাগজের নিত্যদিনের খোরাক। খুব সুচতুরভাবে তিনি তাঁর একটা ‘ফায়ার ব্র্যান্ড’ মূর্তি আলাদা করে নির্মাণ করে কংগ্রেস দলের নিবেদিত সমর্থকদের মধ্যে একটা পাল্টা ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করছিলেন। তিরানব্বই সালের একুশে জুলাই তৎকালীন যুব কংগ্রেসের আয়োজনে গণহিস্টিরিয়ার মতো তাঁর ‘রাইটার্স দখল অভিযান’ কলকাতা শহরের বুকে কয়েকটা তাজা প্রাণ কেড়ে নেয় । রাজ্যের পুলিশের নিশ্চয়ই উচিত ছিল গুলিচালনার আগে আরও সংযত থেকে মারমুখী জনতাকে শান্ত করা, কিন্তু ওইদিন ঘটনাস্থলের খুব কাছে থেকে দাঁড়িয়ে দেখেছিলাম কীভাবে জড়ো হওয়া মানুষকে নেতানেত্রীরা উস্কানি দিয়ে খেপিয়ে তুলছেন। গুলি চালনার পরে ছত্রভঙ্গ ও ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া সমর্থকদের পাশে কিন্তু কেউ ছিলেন না, স্বয়ং মমতা গিয়ে ‘নাকি’ কোনো বেসরকারি নার্সিং হোমে ভর্তি হয়েছিলেন, বেশ কিছুদিন আর তার খোঁজ পাওয়া যায়নি। তবে নব্বই দশকের প্রথমাংশ জুড়ে যেহেতু রাজ্যের প্রধান যুযুধান দুইপক্ষ ছিল বাম আর কংগ্রেস তাঁদের মধ্যে দেওয়াল দখলের যুদ্ধ আর স্লোগানের আড়াআড়ি তো ছিলই। কংগ্রেসের আর্থিক নীতি এবং বিজেপির সাম্প্রদায়িক রাজনীতি দুইই বিদ্ধ হয়েছে তাঁদের তিরে। কংগ্রেস দলও চেষ্টা করেছে শাসক দলকে নানা অভিযোগ তুলে বেকায়দায় ফেলতে —-- বেঙ্গল ল্যাম্প কেলেঙ্কারি, মাটি কেলেঙ্কারি, ট্রেজারি কেলেঙ্কারি এইসব নানা ইস্যু বারবার উঠেছে জনপরিসরে, সংবাদমাধ্যম খবর করেছে । কিন্তু এগুলির খুব পাথুরে প্রমাণ কিছু ছিল না ফলে সাময়িক আলোড়নের বুদবুদ তুলে এগুলো মিলিয়েও গেছে নিজের নিয়মে। মুখ্যমন্ত্রীর পুত্র চন্দন বসুও কখনো কখনো শিরোনামে এসেছেন, প্রশ্ন উঠেছে তার সম্পত্তি নিয়ে —-- কংগ্রেস দেওয়াল লিখেছে ‘বামফ্রন্টের দুটি অবদান নন্দন আর চন্দন’। জ্যোতিবাবুর মতো প্রবল ব্যক্তিত্বের জন্যও বরাদ্দ হয়েছে বেঙ্গল ল্যাম্প ‘কেলেঙ্কারি’ নিয়ে কার্টুন, প্রশান্ত শূরের সঙ্গে মিশেছে জমি ‘কেলেঙ্কারি’ আর একদা জ্যোতিবাবুর আপ্ত সহায়ক তথা আলিপুরের বিধায়ক অশোক বসুকে যুক্ত করা হয়েছে ‘ট্রেজারি কেলেঙ্কারি’ র সঙ্গে। তবু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মূল অভিযোগ ছিল প্রদেশ কংগ্রেসের মাথারা সিপিএমের সরকারের প্রতি ‘নরম’ —- কথাটা একদম ফেলে দেওয়ার মতো ছিল না। সম্প্রতি উত্তর কলকাতার গৌরিবাড়ি এলাকার একদা প্রতাপান্বিত কংগ্রেস বাহুবলী হেমেন মণ্ডল বলেছেন ওই সময়ে প্রদেশ কংগ্রেস ছিল সিপিএমের ‘রক্ষিতা’। এর ফলাফলে আর যাই হোক মমতা একটা নতুন প্ল্যাটফর্ম পেয়ে যাচ্ছিলেন সেটাকেই তিনি ব্যবহার করে গড়ে নিলেন তার নতুন দল। এবং অচিরেই কংগ্রেসের ডি এন এ নিয়ে তিনি হাত ধরলেন বিজেপির—- এন ডি এ নামক যে জোট ১৯৯৮ সালে নির্বাচনে গেল ও জিতে নিল লোকসভা সেখানে তার দল হল প্রধান শরিক এবং মমতা নিজে হাই-প্রোফাইল মন্ত্রী। কার্যত, এখান থেকেই নব্বই দশক দেখা দিল রাজনৈতিক বিচারে রাজ্য রাজনীতির নতুন নিদর্শ হিসেবে। সেই প্রথম ‘চুপচাপ ফুলে ছাপ’ স্লোগান দিয়ে মমতার দল বেশ কিছু আসন পেলেন এবং সিপিএমের দুর্গ বলে পরিচিত কিছু এলাকায় বিজেপি নিজেদের সাংসদকে জিতিয়ে নিতে পারল ও কেন্দ্রে মন্ত্রীও করল। জ্যোতিবাবু বলেছিলেন, মমতার সব থেকে বড় অপরাধ খাল কেটে কুমির আনা (অর্থাৎ বিজেপিকে বাংলায় ডেকে আনা) —-- আজকের মাটিতে দাঁড়িয়ে যখন দেখা যাচ্ছে বিজেপির মতো বিভেদকামী শক্তি বাংলার মাটিতে পোক্ত ভিত গড়েছে তখন এই সমালোচনা ভুল ছিল বলে মনে হয় না। এটাও ঠিক মমতার সাংগঠনিক সাহায্য ও রাজনৈতিক মদত ছাড়া বিজেপি এখানে তাঁদের ঘাঁটি শক্ত করতে পারত না। তবে পাশাপাশি এটাও ঠিক মতাদর্শের দিক দিয়ে একেবারে বিপরীতপ্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকা বামপন্থীরা নিজেদের সদস্য সমর্থকদের অন্তরমহলে যদি উদার মনোভাবের চেতনা জাগরূক করে রাখতেন তাহলে দক্ষিণপন্থার এতটা উত্থান হতে পারত না, সবটাই মমতার দিকে দায় চাপিয়ে তাঁরা তাঁদের ভূমিকা উপেক্ষা করতে পারেন না। নব্বইয়ের প্রান্তভাগে যখন শতাব্দী শেষ হয়ে আসছে তখন রাজ্যের কংগ্রেস প্রায় স্তিমিত, প্রবল বামপন্থা কিছু শিথিল ও বামফ্রন্ট সরকারও রাজ্যে কুড়ি বছর রাজত্ব করে ফেলেছে। কট্টর বাম-বিরোধী কংগ্রেসিরা ক্ষমতার গন্ধ পেয়ে মমতার দলে ভিড়েছেন ও এন ডি এ-র নৌকায় চেপে তাঁর রাজনীতির দুর্বার গতি একটা বার্তা দিতে পারল। মূল কংগ্রেসি স্রোতের বাইরে স্বতন্ত্র দল করে রাজ্যে রাজ্যে অন্য গোষ্ঠীগুলি যখন হতোদ্যম তখন বাংলায় কংগ্রেস-ছুট হিসেবে তিনি সফল। আগামী শতকে এই দিক বদল ধীরে ধীরে নির্ণায়ক হবে বাংলার রাজনীতির। দক্ষিণপন্থী রাজনীতির আশঙ্কার সঙ্গে সঙ্গে বাম ও কংগ্রেস কেন্দ্রীয় স্তরে ক্রমশ কাছে আসছে, যদিও রাজ্যে তার প্রত্যক্ষ ছাপ আবছায়া কারণ বাংলায় কংগ্রেসের সব আলো শুষে নিয়েছেন মমতা, তার ছায়া লম্বা হচ্ছে। শতাব্দী শেষ হল দেওয়ালে আদবানি বাজপেয়ীর ছবির পাশে ততদিনে ‘দিদি’ হয়ে ওঠা মমতার ছবি দিয়ে, প্রকাশ্য হল তীব্র বাম বিরোধী স্লোগান। জ্যোতি বসু রাজ্যের রাজনীতি থেকে অবসর নিলেন। বাংলার রাজনীতি বাংলার দেওয়াল সেজে উঠল নতুন নতুন শব্দে বিচিত্র অক্ষরে পাঁচমিশেলি বার্তায়।ভোটুৎসবে ভাট - হযপচো - সমরেশ মুখার্জী | কিছুদিন ধরে NRC নিয়ে একটু দুশ্চিন্তায় ছিলাম। দুশ্চিন্তা এজন্য নয় যে বাপ ঠাকুরদার দেশে জন্মে দীর্ঘদিন সরকারকে আয়কর ও কয়েকবার ভোট দিয়েও বাঞ্ছিত কাগজ না দেখাতে পেরে ডিটেনশন সেন্টারে গিয়ে শেষ জীবনটা ডোলের মিল খেয়ে বাঁজা কাব্যচর্চা করে কাটাতে হবে। চিন্তা এও নয় যে তাহলে হয়তো বাকি জীবনে কালেভদ্রে বৌ, ছেলের সাথে গরাদের ভেতর থেকেই কথা বলে কাটবে। কারণ বিপুল অর্থব্যয়ে সংঘটিত NRC নামক অর্থহীন পয়জারটাই NRC বা Nothing Really Credible বিবেচিত হয়ে হয়তো আদালতের রায়ে বা সরকার বদলে গিয়ে বাতিল হয়ে যেতে পারে। শেষবেষ যদি তা লাগুও হয় তা আমার জীবদ্দশায় হবে কিনা কে জানে। দুশ্চিন্তার কারণ - কী পদ্ধতিতে তা নির্ধারিত হবে? তখন একদিন হঠাৎ 'হঠাৎ যদি উঠলো কথা' নামক একটি তুমিনল নালা চোখে পড়লো। প্রথমেই নজর কাড়লো সেই নালার নারী নোঙ্গর। তার নাম পৌলমী নাগ। নিবাস উত্তর কলকাতা। পড়াশোনা জয়পুরিয়া কলেজ থেকে সাংবাদিকতা। দেখে মনে হোলো দেশের নানা দূর্নীতি ও অব্যবস্থায় সে এক অসন্তষ্ট হৃষ্টপুষ্ট যুবতী। তার চশমাটি নাক থেকে হড়কে গালে ঠেকনো দিয়ে টিকে থাকে। ফলতঃ ফ্রেমের উপরাংশ তার ধারালো চক্ষুদ্বয়ের উর্ধ্বরেখার সাথে মিলে থাকে। সে যখন ঝুলে পড়া চশমায়, ঝকঝকে দন্তশোভায়, ক্ষুরধার কথায় মানানসই মস্তক সঞ্চালনে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গুরুগম্ভীর ভাবে পেশ করে তখনও আমার তাকে দেখে বেশ মজা লাগে। একথা 'হঠাৎ যদি' পৌলমী শুনতে পায় তাহলে নিশ্চিত আরো অসন্তুষ্ট হয়ে আরো সিরিয়াসলি বলবে - আপনাদের মতো লঘুচিত্ত বুড়োদের জন্যই দেশের আজ এই অবস্থা। সিরিয়াস বিষয়ে সিরিয়াসলি আলোচনা করছি তাও আপনার মজা লাগছে? কিন্তু কী করি। আমার জন্ম বোধহয় ফাজলামি তিথির ফচকেমি লগ্নে রসিকতা নক্ষত্রে, তাই কুষ্টিতে লেখা আছে ইয়ারকি রাশি ও চ্যাংড়ামি গণ। তাই লঘু মজা, খেলো রসিকতা করার জন্য আঙ্গুল, মুখ মুখিয়ে থাকে। মন তো থাকেই। তার চক্ষুদুটিও 'প্রজাতন্ত্র' টিভির মূখ্য পুরুষ নোঙ্গর - 'সাগর গোপতি' সদৃশ বুদ্ধিদীপ্ত। তবে 'হযউক' নালার মহিলা নোঙ্গর 'সাগরের' মতো লাফালাফি বা তর্জনী আস্ফালন করে আড়াইশো ডেসিবেলে গর্জন করেন না। শোনা গেছে নিয়মিত সমূদ্রগর্জন শুনে ছায়াপথের এক দূরবর্তী তারা থেকে - যেখানে মানুষের চেয়ে অনুন্নত কোনো প্রজাতির উদ্ভব হয়েছে - বেতার তরঙ্গে বিপন্ন বার্তা পাঠিয়েছে - "ব্লিপ, ব্লিপ, হ্যালো পৃথিবী, আমরা তোমাদের গ্ৰহ থেকে এক নোঙ্গর 'সাগরের' কথা বেতার তরঙ্গের সাহায্য ছাড়াই সরাসরি শব্দতরঙ্গের মাধ্যমে শুনতে পাচ্ছি, তাই জানতে চাইছি পৃথিবীবাসীর, বিশেষ করে ভারতবাসীর কানের কী অবস্থা?" তো সেই যুবতী নোঙ্গর লম্বা হাতার ব্লাউজে, মার্জিত পোষাকে, পরিমিত প্রসাধনে পরিপাটি হয়ে পরিচ্ছন্ন ভাষায় প্রভূত বিশ্লেষণ সহকারে সেদিনের নির্ধারিত বিষয়ে তার বক্তব্য পেশ করেন। তাই তার কথা শুনতে বেশ লাগে। মনে হয় এনাদের মতো অপেশাদার নোঙ্গরদের দেখে 'মহাসাগর' গোষ্ঠীর পেশাদার নোঙ্গররা কেন বোঝে না যে কেবল গর্জন করলেই বক্তব্যের ওজন বাড়ে না। তাতে থাকা চাই কিছু সারবস্তুও। কারণ দর্শকদের যতটা নির্বোধ ভেবে তারা তাদের ফাঁকির পসরা সাজিয়ে টিভির পর্দায় সাংবাদিকতার নামে বাণিজ্য করতে হাজির হন - সবার না হলেও - অনেকের কাছেই তা রীতিমতো বিরক্তিকর লাগে। হঠাৎ ওঠা কথার মতো অনেক কিছুই হঠাৎ হয়। হঠাৎ আসে অতিমারী। হঠাৎ হারায় চাকরি। হঠাৎ মানুষ প্রেমে পড়ে। হঠাৎ তাকে তোলে ঘরে। হঠাৎ ফুরোয় মোহের ঘোর। হঠাৎ ভাঙে তিথিডোর। এভাবে নানা কিছু বহুদিন ধরে ভোগ, যত্ন, সঞ্চয়, অবহেলা, অপব্যবহার করার পর হঠাৎ কোনো পরিস্থিতি, ঘটনা, কথা, দৃশ্যে হঠাৎই হয় বোধোদয়। রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠে ঘুমচোখে দুফোঁটা আইটোন দিয়ে একটা টুলে বসে আমি ফুট ম্যাসাজারে পা দুটো ঢুকিয়ে দিই। মেশিন কোঁয়াও কোঁয়াও করে ম্যাসাজ করতে থাকে পায়ের পাতা। আমি চোখ বুঁজে আফিমখোর বুড়োর মতো ঝিমোতে থাকি। শরীর থেকে ধীরে ধীরে কেটে যায় বাঁচাবুচা ঘুমের রেশ। তারপর উঠে একটু হাত পা নাড়ি। শরীর নামক যন্ত্রটাকেও তো চালু রাখতে হবে। না হলে করোনার কড়কানি কমলে আবার 'একলা চলো রে' হবে কী করে? আসলে আমি মূলতঃ ঘুমকাতুরে। কোনোকালেই আমার ভোরে উঠতে ভালো লাগে না। অথচ ভোরের মহিমাময় সৌন্দর্য উপভোগ করতেও ভালো লাগে। এ যেন পেটরোগার রাবড়ি ভোজনের বাসনা। ছড়াবে তবু ছাড়বে না। ড্রয়িং রুমের যেখানে বসে রোজ আমার এই প্রাতঃবিলাস হয় তার ডান দিকে পরপর তিন থাক ও বাঁদিকে মেঝেতে পাশাপাশি দুটো কার্ডবোর্ড কার্টন রাখা আছে। পাঁচটাই Amazon Pantry থেকে পাওয়া। কার্টনগুলো ভালো। তাই ফেলিনি। ডানদিকের তিন থাকে থাকে বই ও বেড়ানোর সামগ্ৰী। বাঁদিকের মেঝেতে দুটো কার্টন Items Quarantine Chamber. চায়না, দুবাই থেকে আসা সম্ভাব্য করোনা আক্রান্ত যাত্রীদের মতো দোকান থেকে কেনা মুদীর মালগুলো প্রথমে ঢোকে এক নম্বরে। তিনদিন পড়ে থাকে সেখানে। প্যাকেটের গায়ে করোনো ভাইরাস লেগে থাকলেও কাউকে কামড়াতে না পেরে তিনদিনে তারা অনশনে মারা যাবে। এমনই নিদান দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। যেমন যাচ্ছে (মারা) রাস্তায় কিছু পরিযায়ী শ্রমিক। করোনা আতঙ্কে পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরতে গিয়ে। তারপর দ্রব্যগুলি আসে দু নম্বর কার্টনের সেফ জোনে। বৌমণিকে করোনাকালীন SOP বুঝিয়ে দিয়েছি। তিনি দুনম্বরী বাক্স থেকে মাল নেন। তো সেদিন পা ম্যাসাজ করতে করতে তন্দ্রাজড়ানো চোখ পড়লো ডানদিকের কার্টনে লেখা লোগোটার দিকে। আগে অনেকবার দেখেছি। কিন্তু সেদিন 'হঠাৎ যখন পড়লো চোখে' তখন লোগোটা যেন চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিলো তার তাৎপর্য। হয়তো এ তাৎপর্যের সাথে আমার পরিচিত সবাই বহু আগে থেকেই পরিচিত। আমারই উপলব্ধি হোলো হালে। লেট লতিফ বলে। লোগোর নীচে তীরের ন্যাজটা a তে শুরু হয়ে মুখটা শেষ হয়েছে z তে। তার পর দুটো অক্ষর on. অর্থাৎ লোগোটা যদিও বিখ্যাত বর্ষাবনের নাম তবে সে যেন গ্ৰাহককে বলতে চাইছে - a to z যা চাইবে, on dot পৌঁছে যাবে ঘরে। তীরটাও স্মাইলির মতো - অর্থাৎ be happy, ডু ফূর্তি and be rest assured about on time delivery. বহু বিখ্যাত কোম্পানির নামের আদ্যক্ষর ক্যাপিটাল লেটার - Google, Microsoft, Apple, Volvo, Reliance, Airtel ইত্যাদি। Indigo’র আদ্যক্ষর তো স্বগর্বে ঘোষণা করছে আমিত্ব - I'm the best. কারুর ব্র্যান্ড আবার অল ক্যাপ - TATA, BMW, AMD যদিও শেষোক্ত ব্র্যান্ডের বড়দার ঘোষণা subtle & intelligent - “intel” - কারণ সে জানে তার খেলা চলে insideএ। কিন্তু আমাজনের কারবার বহুজনকে নিয়ে যাদের কারুর আবার বোল্ড, ক্যাপিটাল অক্ষর দেখে চোখ কড়কড় করে। তেমন লোকজন বেশী হয়ে আমাজন বয়কট করলে বেজোসকে বেচাকেনা বন্ধ করতে হবে। তাই হয়তো আমাজনের লোগো অল লোয়ার কেস। আজীবন আমরা নিয়ত বহু কিছু দেখি, শুনি, তবে কখনো 'হযপচো' বা 'হযশুকা' (শুনি কানে) থেকে হঠাৎ হতে পারে 'হযহম' (হলো মনে)। অপ্রত্যাশিত দৃশ্য, আলটপকা কথা, আচমকা উপলব্ধি - এসবের অভিঘাত কখনো হতে পারে অনন্য এবং সূদুরপ্রসারী।বৈঠকি আড্ডায় ১৭ - হীরেন সিংহরায় | লাল নীল হলুদের খেলা ২ভোটের দিন ও তারপরের দিনআমাদের গ্রাম ন্যাপহিলে ভোট নেওয়া হয় স্থানীয় স্কাউট ক্লাবের মাঝারি গোছের একটা ক্লাসরুমের ভেতরে। সেখানে মুখোমুখি দুটি বেঞ্চ পাতা , কয়েকটি চেয়ার , মধ্যিখানে মতদানের দুটি ঘেরাটোপ । দু পাশে দুটো নোটিস বোর্ড, সেখানে মতদাতাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ব্যালট সংগ্রহ করতে হবে তার ঠিকানা অনুযায়ী। কোন পথে বাড়ি ? এ থেকে কে বাঁ দিকে,ডানদিকে এল থেকে জেড। আমাদের রাস্তার নাম লিটলউইক রোড , অতএব দক্ষিণ পন্থা ধরে হাজির হলাম বেঞ্চের ওপাশে অধিষ্ঠিতা মহিলার কাছে। তিনি প্রথমে জানতে চাইলেন রাস্তার নাম পরে আমার নাম । এবারে প্রমান করতে হবে আমিই সে ! সোহম ! ওয়ার রুম ভোটার তালিকায় নাম থাকলে ইলেকশানের দু সপ্তাহ আগে বাড়িতে একটা কার্ড আসে। তাতে ভোটার নম্বর , ভোটিং বুথের ঠিকানা লেখা । ভোট কেন্দ্রে সেটা দেখালেই ব্যালট পেপার পাওয়া যায় , যথাস্থানে টিক দিয়ে বাকসোয় ফেলে দিলে মতদান কর্ম সম্পূর্ণ হয়। কয়েক বছর আগে অবধি কোন পরিচয় দেখাতে হতো না , কার্ডই আমার প্রমাণ পত্র । কার্ড ছাড়াও, শুধু বাড়ির ঠিকানা জানিয়ে ভোট দেওয়া সম্ভব ছিল। কয়েক বছর যাবত ছবি ওলা সবুত দেখানো আবশ্যিক – পাসপোর্ট , ড্রাইভিং লাইসেন্স, লাইব্রেরি কার্ড যেটা খুশি । আজ আমি কোনোটাই আনি নি , অগত্যা আমার সিনিয়র বাস পাস দেখিয়ে ভোট দিলাম। এবারে আমাদের টেলিং এর কাজ শুরু। বুথে ঠিক ঢোকার মুখে আমার বসার জন্য নিজের হাতে চেয়ার নিয়ে এগোয়ে এলেন প্রিসাইডিঙ অফিসার স্বয়ং । ইতিমধ্যে অন্য দুই যুযুধান পক্ষ মঞ্চে আবির্ভূত : লেবার পার্টির প্রতিনিধি ড্যান সাম্পসন এবং কনজারভেটিভ দলের প্রার্থী সাজ হুসেন ; তিনি আমাদের স্থানীয় সাব পোস্ট মাষ্টার। বারো বছর যাবত জিতে আসছেন এই সিটে । এবার লিবারাল ডেমোক্র্যাট দলের নিশানায় আছেন তিনি। আমাদের ক্যান্ডিডেট জন পিয়ারস প্রথম ভোট যুদ্ধে নেমেছেন , তিন টার্মের সিটিং কাউনসিলরকে হারানো যে শক্ত কাজ সেটা আমরা সকলেই অনুধাবন করেছি । তবু বুকে বল বেঁধে হও অগ্রসর।লেবারের ড্যান সাম্পসনের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল চট করে , তাঁর মা রোমানিয়ান । বুখারেসট শহর নিয়ে গল্প হলো – বর্তমানে সে শহর ইউরোপের টুরিস্ট তালিকার শীর্ষস্থানে অবস্থান করছে। এমন সময়ে স্থানীয় প্রকাশক জন ডেভিস এলেন । আমাদের কেউ চা কফি দেয় নি দেখে তাঁর গাড়ি নিয়ে গিয়ে তৎক্ষণাৎ কোথা থেকে কাগজের কাপে কফি যোগাড় করে আনলেন। কিন্তু এতো আয়োজন যাদের জন্য সেই ভোটার কোথায় ?সকাল থেকে অন্ধকার হয়ে আছে আকাশ। কে বলবে এটা মে মাস? বুথের ভেতরে ছ জন কর্মী, হলে আমরা চারজন। শুধু ভোটার কম পড়িয়াছে! অনেকদিন আগে দেশে দেখা একটা ছবি মনে পড়ে গেল – আই এস জোহরের একটা কলাম ছিল ফিল্ম ফেয়ারে , তাতে কার্টুন :ফার্স্ট ক্লাস কামরায় একজন যাত্রী বসে আছেন তাঁকে ঘিরে কন্ডাক্টর , চা ওলা সহ আরও কয়েকজন। নিচে মন্তব্য - উই অলওয়েজ হ্যাভ মোর পিপল সারভিং ওয়ান কাসটমার !এক ঘণ্টায় পাঁচজন ভোট দিলেন। আমার বদলি সাইমন এলে আমার দু ঘণ্টার ছুটি হলো। কানালসাইড পরের স্টপ মেবেরি সেন্টার, কানালসাইড । এটি একটি ছোটো খাটো কনফারেন্স হল এবং লাইব্রেরি । উওকিং হিস্টরি সোসাইটির সদস্য হিসেবে মাসের প্রথম সোমবারের মিটিঙে আসি , তাই বেশ চেনা । ব্যবস্থা চমৎকার । বুথের ঠিক বাইরে একটা টেরাসে চেয়ার টেবিল পাতা, তার একটি দখল করা গেল সহজেই। কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে কোথা থেকে চা কফি আসতে থাকে কাগজের কাপে । মুহুর্মুহু মতদাতা আসছেন , তাল দেওয়া ভার । উৎসবের আবহাওয়া । লেবার দলের হয়ে টেলিং করছেন একজন, আমার উলটোদিকে । তাঁর হাতে মোবাইল ফোন , প্রায় সর্বদা মেসেজ আসছে ,মাঝে মাঝেই উঠে যাচ্ছেন কথা বলতে । ফিরে এসে জানতে চাইছেন তিনি কোন কোন ভোটারকে মিস করলেন, তাঁদের নম্বর গুলো যদি তাঁকেও জানিয়ে দিই! এ ব্যাপারে সমস্ত প্রতিযোগী দলের মধ্যে একটা সমঝোতা থাকে , আমরা এ তথ্য শেয়ার করি । আলাপ হলো, নাম তালাত। এক সময়ে বললেন ‘ নিজের ব্যবসা আর টেলিং এ দুটো একসঙ্গে সামলানো বেশ কঠিন ব্যাপার । জানেন সকাল আটটা থেকে এখানে বসে আছি ! কখন যে কেউ এসে আমাকে ছুটি দেবে জানি না ‘ অবাক হয়ে বললাম, ‘ সে কি ! আপনার ডিউটি শিট নেই ?’ তালাত হেসে বললেন, ‘ ডিউটি শিট ? আমার শালা তাহির ইলেকশন লড়ছে ! তার সেবা করাটাই আমার ডিউটি !’লাল (লেবার ) এবং হলুদ (লিব ডেম) হাজির কিন্তু নীলের(কনজারভেটিভ ) দেখা নেই । দেওয়াল লিখন তাঁরা ভোরবেলায় পড়ে নিয়েছেন।ভোটাররা বেশির ভাগ আমাদের উপ মহাদেশের কোন না কোন দেশ থেকে এসেছেন । বুথে ঢুকবার পথে অত্যন্ত ভদ্র ভাবে অনেকে তাঁদের ভোটার কার্ড আমাদের দিকে এগিয়ে দিলেন , আমরা জানালাম ওটা মতদানের পরে দেবেন। দুজন ভোটদাতা নীরবে আমার কোটের হলুদ ব্যাজটি ছুঁয়ে ইশারা করে জানালেন তাঁরা কাকে ভোট দেবেন ! এ ধরণের কোন বাক্যালাপ অবশ্যই নিষিদ্ধ, তবু জেনে ভালো লাগল! পরিবেশটি ভারি সুন্দর , বাংলা হিন্দি উর্দু গুজরাতি শোনা যায় চতুর্দিকে। সম্পুর্ন অপরিচিত ভোটার সামনে এসে দাঁড়ান ; ‘ সেলাম আলায়কুম’ , ‘ কেমন আছেন’ ‘কেম ছো ‘ ইত্যাদি নানান সৌহার্দ্য বিনিময় হতে থাকে । ছোটো কমিউনিটি , অনেকে পরস্পরকে চেনেন, রীতিমত উৎসবের হাওয়া চলছে যেন । দু একজন আবার গল্প জুড়ে দেন, যেটা ঠিক কেতাব সম্মত নয় ।আমি বদলি টেলারের আশায় আছি, লুইজার ফোন এলো । আমার পরবর্তী স্টেশন শিয়ারওয়াটার কিন্তু আমি কি এই মেবেরিতে থেকে যেতে পারি অতিরিক্ত দু ঘণ্টা ? এমনি করে দিন গড়িয়ে সন্ধ্যে! শিয়ারওয়াটারে আমাদের সদস্যা টিনার কাছে শুনলাম- তিনি ন্যাপহিলের লেবার প্রার্থীর বাবাকে কোনো সূত্রে চেনেন । সেই বৃদ্ধ মানুষটি গত কয়েক দিন যাবত একগাদা লিফলেট নিয়ে দোরে দোরে ঘুরছেন। টিনাকে সামনে পেয়ে বলেছেন , ছেলের জন্যে এই বোঝা ঘাড়ে নিতে হয়েছে ! আমার বয়েস পঁপ্রায় আশি হলো , লেবার পার্টির কোন ক্যাডার নেই। ছেলে সবটাই ধরিয়ে দিয়েছে আমার হাতে , তার নাকি লন্ডনে জরুরি মিটিং থেকে রোজ।ভোট গণনা হবে উওকিং লেজার সেন্টারে, সেখানে প্রবেশ বাই ইনভিটেশান ওনলি, কত রাতে যে শুরু হবে জানা নেই। আমি একা বাড়িতে, কুকুরের পাহারায়। টেলিভিশনে মন দিলাম।১৯৯৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে লেবারের ল্যান্ডস্লাইড বিজয় দেখেছি। হাওয়া কোনদিকে বইছে তার আঁচ অনেক আগেই পাওয়া গিয়েছিল। ঋষি সুনাকের কনজারভেটিভ পার্টি এবার যে গোটা দেশে সম্পূর্ণ ভোট ডুবির দিকে দ্রুত নৌকা বাইছে সেটা বুঝতে জ্যোতিষীর শরণাপন্ন হতে হয় না । যেমন যেমন রাত বাড়ে , টেলিভিশনে কনজারভেটিভদের দুর্গ ভেঙ্গে পড়ার খবর আসতে থাকে । রাত তিনটে নাগাদ দেখা গেলো সারা দেশের পৌরসভা নির্বাচনে মোট কাউনসিলরের সংখ্যার হিসেবে লিবারাল ডেমোক্র্যাট দল লেবারের পরেই দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী -ইংল্যান্ডে পাঁচশোর বেশি কনজারভেটিভ কাউনসিলর তাঁদের কাউসেলিং করার অধিকার হারালেন , পার্টি হারালো বারোটি পৌরসভার মেজরিটি। লন্ডন ম্যানচেস্টার লিভারপুলে সরাসরি মেয়রের নির্বাচন হয়, লেবার জিতেছে সর্বত্র । আঞ্চলিক মেয়র নির্বাচিত হন উত্তরে টিস ভ্যালি , ইস্ট মিডল্যানডস, ওয়েস্ট মিডল্যানডস, নর্থ ইস্ট ইংল্যান্ড , ওয়েস্ট এবং সাউথ ইয়র্কশায়ার। টিস ভ্যালি বাদে বাকি গুলি জেতে লেবার পার্টি । শুক্রবার ভোরবেলায় টিস ভ্যালির পুনঃ নির্বাচিত মেয়র সবে ধন নীলমনি বেন হাউখেনকে অভিনন্দন জানাতে হেলিকপ্টারে চড়ে ঋষি হাজির হয়ে সেখানকার বিমান বন্দরের ভাষণে বললেন, আমাদের পার্টির কাছে এই বিজয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটা প্রমাণ করে যে মানুষ আমাদের ওপর বিশ্বাস রাখেন। একমাত্র আমরাই দেশকে এগিয়ে নিয়ে জেতে পারি । উই হ্যাভ এ প্ল্যান !জলে ডোবার আগে খড় কুটোকে আঁকড়ে ধরার প্রচেষ্টা চিরন্তন। সারা দেশের ভোট গণনা শেষ হতে সকাল। প্রিসাইডিঙ অফিসার একেক বার মাইক দখল করে ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড ফলাফল ঘোষণা করেন । দশটি আসনের ন’টিতে লিব ডেম বিজয়ী। সবচেয়ে বড়ো সাফল্য- বারো বছরের সিটিং কাউন্সিলর ন্যাপহিলের পোস্ট মাষ্টার সাজ হুসেনকে হারালেন স্থানীয় রাজনীতিতে সম্পূর্ণ নতুন চেহারা জন পিয়ারস । তিনি ও আমি একত্রে জন গণেশের দুয়ার প্রদক্ষিণ করেছি কিন্তু ভাবতে পারি নি ষাট পেরুনো এক রিটায়ার্ড আই টি এঞ্জিনিয়ার সমাজে পরিচিত মুখ এক পোস্ট মাষ্টারকে দুশো ভোটের ব্যবধানে তাঁর আসন থেকে সরাতে পারবেন ! বোধহয় লেবার প্রধান মন্ত্রী হ্যারলড উইলসন বলেছিলেন, এ উইক ইজ এ লং টাইম ইন পলিটিক্স। গণনার ফল ঘোষণা কানালসাইড ওয়ার্ডে সিটিং কাউন্সিলর তাহির আজিজ আমাদের প্রার্থী ফয়জল মুমতাজের বিরুদ্ধে ২৯ ভোটে পরাস্ত হলেন। বাইফ্লিট ও ওয়েস্ট বাইফ্লিট আসনে লিব ডেম সমর্থিত নির্দলীয় প্রার্থী স্টিভ হাওস হারালেন সিটিং টোরি পার্টি কাউন্সিলর জশ ব্রাউনকে। একটি সম্পূর্ণ অচেনা অজানা ওয়ার্ডে ৩৪৯টি ভোট হাসিল করে মায়া তাঁর জয়ের পথ সুগম করে দিলো । মায়ার রেজাল্ট চার বছর আগে তিরিশ জনের কাউন্সিলে তাদের ছিল ষোল জন সদস্য । এবে উওকিং কাউন্সিল কনজারভেটিভ মুক্ত। শেষ ছবি Woking Borough Council Political make-up সামগ্রিক ভোটের ফল Elections 2024 England Council result পুঃ বুধবার তেইশে মে বিকেলে দশ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক সাধারণ নির্বাচনের দিন ঘোষণা করলেন- ৪ জুলাই । ফলত সব পার্টি শিবিরে রীতিমত সাজো সাজো রব পড়ে গেছে ; সামনের সাত সপ্তাহ আদা জল খেয়ে কাজ করার ঘণ্টা বেজেছে।প্রসঙ্গত , গ্রীষ্মকালে ব্রিটেনে কখনো সাধারণ নির্বাচন হয় না - স্কুলের ছুটি, ক্রিকেট , উইম্বলডন টেনিস, ব্রিটিশ ওপেন গলফ, গ্লাইনডবোরনের অপেরা ( তার সঙ্গে যোগ করুন এবারের ইউরো ২০২৪ ফুটবল , প্যারিস অলিম্পিক ) ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত থাকেন মতদাতারা। বিগত একশো বছরে এই ট্র্যাডিশনের একটি মাত্র ব্যতিক্রম দেখা গেছে:৮ মে , ১৯৪৫ জার্মানির নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের কয়েকদিন বাদে প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল ৫ই জুলাই নির্বাচনের দিন ঘোষণা করলেন । চার্চিল সদ্য এক বিশাল রণে বিজয়ী হয়েছেন ; ভোট যুদ্ধে কৃতজ্ঞ দেশবাসী যে তাঁকে ও তাঁর দলকে বিপুল সমর্থন জানাবেন এ বিষয়ে তাঁর মনে কোন সংশয় ছিল না।রাত পোহালে দেখা গেল কনজারভেটিভরা হারালেন দেড়শর বেশি আসন , তাদের পিছনে ফেলে প্রথমবার পার্লামেন্টে নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করল ক্লিমেনট অ্যাটলির লেবার পার্টি ( ৩৯৩-১৯৭ )।এক ঋষি আমাদের প্রধানমন্ত্রী। নিশ্চয় অনেক ভেবে চিন্তেই তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।
জনতার খেরোর খাতা...
মনুষ্যত্বের গর্ব - প্রত্যয় ভুক্ত | গর্বের মাস?- এই যে এই বিপুল পৃথিবী, নানা জায়গায় নানা মানুষ, নানা ধর্ম-সংস্কৃতি, নানা ধরনের মন মানসিকতা, সেই মিশ্রণে মিশে আছি আমি, আমরা; দিকে দিকে মানুষের দিগন্ত, জীবের চেতনার দিগন্ত নিয়ত উন্মোচিত হচ্ছে, আলো-অন্ধকার-ছায়ার খেলা চলেছে নিরন্তর আমাদের চিত্তলোকে। এখন পৃথিবীতে বড়ো সুখের সময় নয় সত্যি। জরতী পৃথিবীর অন্নপাত্র নিঃশেষপ্রায়, দিকে দিকে চিতার আগুনের হল্কা মুখে এসে লাগে, পোড়া মাংসের গন্ধে শ্বাস নিতে কষ্ট হয়, গরম বাতাসের দীর্ঘনিশ্বাসে চোখের জল ও শুষে নেয় উষর মাটি, তারি মধ্যে চিৎকৃত শিবারব আমাদের চিত্ত বৈকল্য ঘটায়, সত্য-সুন্দর-শিব, শান্ত-শুভ-অদ্বৈতের যে শ্বাশ্বত আদর্শ মানুষের তার বিপরীতে এমন শ্রীহীন কুৎসিত অশ্লীল স্ব-প্রদর্শনী ও তীব্র সম্ভোগপ্রবণতা, শ্মশানের মধ্যে একনাগাড়ে উচ্চনিনাদে নিজেকে বিজ্ঞাপিত/পণ্যায়িত করার ও অপরকে 'অপর' বানানোর আর দাবিয়ে রাখার এমন বিষম প্রবণতা চিরন্তন মানবপ্রকৃতির অন্তরাত্মাকে পর্যন্ত কলুষিত করে তোলে, ক্রমশ যেন মুক্তির দুয়ারগুলি বাইরে রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে মনে হয়। তাই এবার, এইসব ব্যাক্তিগত ও বিশ্বব্যাপী বিপর্যয়গুলির মুহূর্তে ফিরে তাকাই আপন অন্তরের পানে, প্রথম প্রথম আলো ঠেকে না অনভ্যস্ত চোখে-মন বিমর্ষ ও বিরূপ হয়ে ওঠে, আপন চিত্তদৈন্যের ধিক্কারে মন বিকল হয়ে আসে, সব আশাই যেন হারায় অতল আঁধারে। কিন্তু জানি, আছে আনন্দনিকেতন, নিজের মধ্যেই আছে-কত দূরে জানিনা, কিন্তু তারি মলয় বাতাস কখনো গায়ে এসে লাগে বৃষ্টির পরের বসন্তবিকালের দখিনা বাতাসে, একলা রাতের গভীর ভেজায়, বুদ্ধপূর্ণিমার রাতের চাঁপা-গন্ধরাজ-রজনীগন্ধার সুবাসে। প্রকৃতি নিরুত্তাপ, নির্বিকার আমাদের এই একলা প্রাণের গোপন সব দুঃখ, মানবের নিরন্তর সংঘর্ষ আপন সত্তার সাথে-আদিমের সাথে অর্বাচীনের, বর্বরের সাথে সুন্দরের, সত্যের সাথে মোহের, জ্ঞানের সাথে মূঢ়তার, তথ্যনিষ্ঠার সাথে সংস্কারের, বিশ্বাসের সাথে সংশয়ের, গর্বের সাথে লজ্জার এই যে সব সতত ক্রিয়াশীল দ্বান্দ্বিক বিরোধ-সমন্বয়, আমাদের ক্রমেই মানুষ হিসেবে গড়ে তুলছে বা ভাঙছে- তার সাথে আপাত সম্পর্করহিত এই বিস্তৃত বহিঃপ্রকৃতি।কিন্তু এ আপনার এবং আমাদের অজানিতে আমাদের অন্তঃপ্রকৃতিকে নিয়ত আলোড়িত ও প্রভাবিত করছে- আমাদের সৌন্দর্যপিপাসু মনে সৌন্দর্যবোধকে জাগিয়ে তুলছে জ্যোৎস্নাদীধিতি বিধৌত পূর্ণিমা বা জীবের প্রাণরক্ষার সংগ্রাম আর জীবনের অনিত্যতা সম্বন্ধে অহরহ সচেতন করে তুলছে এই বিশাল পার্থিব সংহারযজ্ঞ- যেখানে কেবলি বিভেদ জীবের সাথে জীবের মৌলিক প্রকৃতিতে, একের উপর অন্যের এই অধিকার স্থাপনের প্রয়াস প্রেম-প্রীতি বা হিংসার আশ্রয়ে, এসবকিছুই নিত্যই আমাদের অবচেতনে নব নব ভাব, ভাবনা, জিগীষার উন্মেষ ঘটাচ্ছে- তাই বাহ্যপ্রকৃতি ও মানবের অন্তঃপ্রকৃতি অঙ্গাঙ্গীভাবে সংশ্লিষ্ট। এবার তাই ফিরে চাইছি মানবের হিংসা-রিরংসা-প্রণয়-ক্ষোভ দীর্ণ জগৎ থেকে আপন নিভৃত অন্তর্জগৎটির পানে, আর এই সসাগর জীবের, সৌন্দর্যের ও বিরাটের আকর এই বহু বৈচিত্র্যময় পৃথিবী, তারও সীমানার বাইরে যে মহাবিশ্ব তার নৈসর্গিক আলো-অন্ধকারের পানে, ইন্দ্রিয়াতীত সব অনুভব, প্রজ্ঞা এবং বোধির পানে।সেখানে হোক আমাদের সত্য আশ্রয়- যে বাহ্যিক বিরুদ্ধশক্তিগুলি ক্রমাগত খর্ব করছে মানবের মহতী শ্বাশ্বতী অধিকারগুলিকে, অবমাননা করছে মানবের পরমসত্তার, সেগুলির বিপ্রতীপে আমাদের অভিযান হোক কঠোর, বন্ধুর পথে, মলিনতা, অসত্য, ভীতি, বাইরের কলঙ্ক ও অন্তরের লজ্জা ত্যাগ করে আমাদের নিভৃত সাধনা হোক ক্রমশ সেই বিরাট মানুষটি হয়ে ওঠার যে আমাদের অন্তরে সুপ্ত এবং গুপ্ত, প্রবুদ্ধ এবং প্রকাশিত হবার ঐকান্তিক প্রতীক্ষায়। বাইরের ক্ষুদ্রতা যেন আমাদের অন্তরের ঐশ্বর্যগুলিকে ম্লান না করে, হাটের ধুলা মার্জনা করতে পারি যেন নির্জনে সুরধুনীর ধারায়, মলিন বসনখানি ত্যাগ করে প্রেমের বসনখানি যেন নিতে পারি নিজদেহে, আর সমবেতভাবে উপনীত হতে পারি সেই সত্যের পথে দেবযানে, ব্যাষ্টিসত্তার স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেও যেন মিলতে পারি সমষ্টির মাঝারে, একাত্মভাবে প্রার্থনা করতে পারি-" অপাবৃণু"; হে বিরাট, হে উদার, উন্মোচিত কর হিরন্ময় আবরণ, সত্যের মুখটি, দুয়ারটি খুলে দাও, "তমসো মা জ্যোতির্গময়" অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে যাও এবং আলোর জ্যোতিতে চোখ ধাঁধিয়ে ভুলিয়ে দিয়ো না, নিয়ে চলো আলো-অন্ধকার, শুভ-অশুভ, শুচি-অশুচি, অজ্ঞান-জ্ঞানের দ্বৈতের পরপারে অদ্বৈতে, তোমার প্রকাশ হোক আমাদের মাঝে ও আমরাও প্রকাশিত হই তোমার আলোকে, জগতের সবকিছুই আমাদের দৃষ্টিতে তোমার জ্যোতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠুক। এই গর্বের মাসের সূচনায়, বাইরের এই ক্লেদ, গ্লানি আর কদন্নের মুষ্টিভিক্ষার থালি ত্যাগ করে যেন উপভোগ করতে পারি ভূমাব্যাপিত তোমার এবং তার সাথে এক ও অভিন্ন একক আমার ও সম্মিলিত সকলের আনন্দকে, স্থিত হই স্ব-তে, আমাদের গর্ব হোক তোমারি গর্ব হে নাথ, হে জীবনস্বামী, এই গর্ব হউক আমাদের অন্তে-তোমারে চেয়েছি, চেয়েছি নিজেকে, বহন করেছি সুকঠিন দায়িত্বের ভার মনুষ্যত্বের, নিজেদের, আপন সত্যে, অনন্তের মাঝে, বাইরের জীর্ণতা, দীনতায় মানবনা অন্তরের নিত্য মানবের পরাজয় , মর্যাদার পরাভব। ক্ষুরধার শঙ্কিল পঙ্কিল বাট, কিন্তু পেরিয়ে যেন যাই হে প্রভু, পেরিয়ে যেন যাই এই নিজেরই ওপর, আমাদের ওপর, তোমার ওপর দৃঢ় বিশ্বাসে ভর করে।ললিত কলা - Sabita Sen | বাসু চৌধুরির বসার ঘর থেকে তুমুল হাসির হট্টগোল শোনা যাচ্ছে। সেখানে এক ঘর মহিলা ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছে, বিভিন্ন বয়সী। বাসু চৌধুরীর বউ সুমিত্রা, ওদের ছেলের বউ কেতকী, তার বোন সোনা। এছাড়া সুমিত্রার দুই বান্ধবী – ইরা আর বনলতা। আরও একজন আছেন যিনি আধঘণ্টা আগেই কলকাতা থেকে এসে পৌঁছেছেন। তিনি সুমিত্রার স্কুল জীবনের অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু – রুচিরা। একদা অতীব সুন্দরী এবং সপ্রতিভ। তিনিই আজকের আড্ডার মধ্যমণি। ওকে উপলক্ষ্য করেই আজকের জমায়েত।রুচিরা একে একে সব পুরোনো বন্ধুদের খবরাখবর নিতে লাগলো। অনেকদিন বাদে পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা। যাদের সঙ্গে দেখা হোলো না তাদের কথা মনের মধ্যে ভীড় করে আসছে। সুমিত্রাকে প্রশ্ন করে, ‘‘তপতীর কি খবর? ও কি এখনও বিদেশেই আছে? অসীমের তো ক্যান্সার হয়েছিলো, এখন কেমন আছে?’’সুমিত্রা জানালো, ‘‘বিদেশে চিকিৎসার পর এখন ভালো আছি।’’ এবার ইরা মুখ খুললো, – ‘‘রুচিরা, একটা কথা বলবো, কিছু মনে করবি না তো? তোর তো অনেক হতাশ প্রেমিক ছিলো। সবাইকে টপকে তুই তো অমিতাভকেই বিয়ে করলি। সেই তারা সব কেমন আছে? দেখা হয় তাদের সঙ্গে?’’‘‘ – নারে, কারো সঙ্গেই দেখা হয় না। লোকমুখে কারো কারো খবর পাই। রথীন তো আমেরিকায় পাকাপাকি ভাবে বাস করছে, মেমসায়েব বিয়ে করেছে। আমাদের সেই রথীন – চাকদার গণ্ডগ্রামের ছেলে, এখন পাক্কা সাহেব। শুনেছি, অতীনের প্রথম বিয়েটা ভেঙ্গে গেছে। আবার বিয়ে করেছে। দুই পক্ষ মিলিয়ে ওর ছয়টা বাচ্চা।’’‘‘সেকিরে, ছয়, ছটি বাচ্চা!’’ হেসে গড়িয়ে পড়লো বনলতা। আমরা তো, একটি দুটিতেই হয়রান!’’মেয়েদের কলতানে আকৃষ্ট হয়ে ড্রইংরুমে এবার বাসু চৌধুরীর প্রবেশ। ‘‘কি ব্যাপার? এতো হাসি কিসের?’’‘‘বাসুদা, আমরা রুচিরার পুরোনো হতাশ প্রেমিকদের কথা বলছিলাম।’’‘‘আরে একসময় তো আমিও সেই দলে ছিলাম। আমার বৌ কোথায় রে? শুনতে পায়নি তো?’’মেয়ে দঙ্গলের মধ্যে থেকে বৌ চেঁচিয়ে বললো, ‘‘না না, আমি কিছু শুনতে পাইনি।’’ আর এক প্রস্থ হাসির রোল উঠলো। বাসুদার বেশ মুড এসে গেছে মনে হয়। - ‘‘কি বলবো আর, একদিন জানতে পারলাম, আমার ছোটভাই, হতচ্ছাড়া ললিতটাও নাকি সেই লাইনে আছে। অগত্যা জায়গা ছেড়ে বেরিয়ে এলাম।’’রুচিরার হঠাৎই মনে পড়লো ললিতের কথা। বললো, ‘‘বাসুদা, ললিতের খবর কি? কোথায় আছে? কেমন আছে?’’বাসুদা – ‘‘ভালো আছে। বিয়ে করে কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে সুখে ঘরসংসার করছে।’’রুচিরা – ‘‘ও কি চাকরী করে? কোথায় করে?’’বাসুদা – ‘‘না, ও স্বাধীনভাবে নিজে ব্যবসা করে।’’রুচিরা – ‘কিসের ব্যবসা?’’ বাসুদা – ‘‘বাজারের সবচেয়ে বড় মুদি দোকানটার মালিক হচ্ছে ললিত।’’ইরা – ‘‘রুচিরা, আমরা তো ললিত সম্পর্কে কিছুই জানি না। তুই কিছু বল ওর সম্পর্কে।’’- ‘‘তোমরা বলাবলি করো, আমি ততক্ষণে একটা দরকারী কাজ সেরে আসি’’ - বলে বাসুদা চলে গেলো।অগত্যা রুচিরা গল্পের ঝাঁপি খুললো। ‘‘যতোদূর মনে পড়ছে, ললিত এই বাড়ীর ছোট ছেলে, বাসুদার সবচেয়ে ছোট ভাই, একটু আদরে বাঁদর, বিদ্যে ক্লাশ টেন পর্য্যন্ত। আমার সঙ্গে আলাপ সুমিত্রার বিয়ের সময়। আমি সুমিত্রার বন্ধু, তাই আমার যত্নআত্তির দায়িত্বটা ও নিজেই নিয়ে নিলো। পরিবেশনের সময় নিজে দাঁড়িয়ে থেকে আমার খাওয়ার তদারক করলো। মিষ্টি লাল দইএর হাঁড়ি থেকে সরটুকু উঠিয়ে আমার পাতে দিলো। আমি যতো বলি – ‘‘না, না, আমি এতো খেতে পারবো না – কে শোনে কার কথা। সুমিত্রা, বাকিটা তুই বল।’’সুমিত্রা একটু এগিয়ে এসে বসলো। - ‘‘আমার দেওরটা বুঝলি, একটু রোমান্টিক গোছের। ওর গায়ের রঙটা একটু চাপা – কিন্তু চোখে মুখে বুদ্ধির ছাপ, কথাবার্তায় চৌখস। পোষাকে ছিলো খুবই সৌখীন। পায়ের চটি থেকে মাথার ক্যাপটি পর্য্যন্ত সব ঝকঝকে সাদা। সুন্দরী মেয়েদের বড়ই পছন্দ করে। হৃদয়ে চিরবসন্ত।‘‘যাই হোক, আমার বিয়ে শেষ হোলো, কিন্তু ললিতের মনে রুচিরাকে নিয়ে আগ্রহ শেষ হোলো না।‘‘ততোদিনে রুচিরার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে, অমিতাভর সঙ্গে। ঘটা করে আশীর্বাদ অনুষ্ঠান করছেন রুচিরার বাবা মা। সেখানে নিমন্ত্রিত হয়ে এলো রুচিরা আর অমিতাভ, সঙ্গে ললিত। আনুষ্ঠানিক ভাবে আশীর্বাদপর্ব শেষ হলে, চলতে লাগলো খাওয়া দাওয়া, গল্প, গান। এরই মধ্যে ললিত রুচিরার সঙ্গে একান্তে একটু কথা বলে নিলো।‘‘আমাকে কি আপনার খুব অযোগ্য বলে মনে হয়? আমি কিন্তু আপনাকে ভালোবাসি – প্রথম দিন থেকেই।’’রুচিরার হতভম্ব ভাবটা কাটতে একটু সময় লাগলো। তারপর গলা ঝেড়ে বললো, ‘‘ইয়ে, মানে – আপনার একটু দেরী হয়ে গেছে। আমার বিয়ের পাত্র এবং দিনক্ষণও স্থির হয়ে গেছে। দেখছেন তো সবকিছু।’’‘‘আমি দেরীতে এসেছি এটা আমার অপরাধ নয়। আমি এগিয়ে আছি ভালোবাসা আর একনিষ্ঠতার জোরে। আপনি আমাকে ফিরিয়ে দিলে, আমার জীবনটা শেষ হয়ে যাবে।’’রুচিরা একটু মুচকি হেসে বললো, ‘‘কিচ্ছু শেষ হবে না। আপনার দিব্যি একটি লাল টুকটুকে বউ হবে। সুখে জীবন কাটবে। এখন ওদিকে চলুন। কে যেন গান গাইছে, শুনতে হবে।’’ ললিতের দিবাস্বপ্ন ভেঙ্গে খান খান।সোনা বাচ্চা মেয়ে, কৌতুহল বেশী – ‘‘রুচিরাদি, তোমার সঙ্গে ওর আর কখনো দেখা হয়নি?’’উত্তরটা দিলো সুমিত্রা – ‘‘হয়নি আবার! বিয়ের আগে রুচিরা একটা স্কুলে পড়াতো। রিক্সা করে স্কুলে যাবার সময় প্রত্যেকদিন ও দেখতে পেতো, ললিত কয়েকজন বন্ধু নিয়ে লীচুতলার মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে – ওর দিকে তাকিয়ে আছে অনিমেষ নয়নে। বন্ধুগুলো মাঝে মাঝে কিছু সরস মন্তব্য ছুঁড়ে দিতো।এভাবে চলতে চলতে একদিন রুচিরার বিয়ের দিনটি এসে গেলো। বিয়ে হয়ে গেলো অমিতাভর সঙ্গে – যে ছিলো ওর বন্ধু, সহপাঠী এবং প্রেমিক। ওরা সংসার পাতলো বোম্বাই, মানে আজকের মুম্বাইতে।তারপর সংসারের জটিল আবর্তে কে যে কোথায় ছিটকে গেলো – সেই খবর আর রাখা হয়নি।এতো বছর বাদে – সবার চুলে রূপোলী রেখা, মুখে চোখে অভিজ্ঞতার ছাপ। পুরোনো দিনের কথা, পুরোনো বন্ধুদের স্মৃতি – মনে হলে বুকের মধ্যে এক অচিন সুর বাজতে থাকে।সবাই চুপচাপ রুচিরার কথা শুনলো। বনলতা নীরবতা ভঙ্গ করলো – ‘‘সুমিত্রা, তোমার ছোট দেওরের সঙ্গে আমরা পরিচিত হতে চাই। ওকে এখানে ডাকলে কেমন হয়?’’ সব মেয়েরা সমস্বরে প্রস্তাবটি সমর্থন করলো। সুমিত্রার মুখে চোখে একটু দুষ্টুমি। বললো, - ‘‘ডাক পাঠাই। দেখি আসে কিনা।’’ এবং ডাক পাঠানো হোলো।ততক্ষণে মহিলারা সবাই একথা সেকথা – তারপর চা সহযোগে চালতার আচারের জটিল রেসিপি নিয়ে আলোচনা করতে লাগলো। কারণ সুমিত্রার বাড়ীতে একটি ফলবতী চালতা গাছ আছে – ও সব বন্ধুদেরকে একটা করে চালতা উপহার দেবে বলেছে।এই সময় ভেজানো দরজার পেছনে চটির শব্দ হোলো। ঘরের সবাই সচকিত। একজন মাঝবয়সী ভদ্রলোকের প্রবেশ ঘটলো। গায়ে একটা চকরাবকরা হাওয়াই শার্ট, আধময়লা পাজামা, মাথায় মৃদু টাকের আভাস। চোখে মুখে অবশ্য সেই পুরোনো সপ্রতিভ ভাবটি এখনও বজায় আছে। প্রথমটায় একঘর মহিলা এবং একটি নতুন মুখ দেখে একটু হকচকিয়ে গিয়েছিলো বটে, তারপরেই সামলে নিলো। সুমিত্রা খুশী মনে ডাকলো, - ‘‘এসো ললিত, ভেতরে এসো। আজ তোমাকে আমরা একজন নতুন মানুষের সঙ্গে আলাপ করাবো বলে ডেকেছি।’’ললিত নতুন মানুষটির দিকে ভালো করে তাকালো – মাথায় রুপোলী ছোপের সঙ্গে চওড়া সিঁদুর, হাতে শাঁখাপলা, পরনে দামী জামদানী শাড়ী, ফরসা মুখে হালকা লিপষ্টিক। ভাবলো, কে এই বয়স্কা সুন্দরী? ওর অবস্থা দেখে সুমিত্রার দয়া হোলো – বললো, - ‘‘ইনি আমার স্কুলবেলার বন্ধু। অনেকবার এসেছেন আমাদের বাড়ীতে।’’ এবার রুচিরার দিকে বললো, ‘‘ও হচ্ছে ললিত, আমার ছোট দেওর।’’এসব শুনে ললিত আর দেরী না করে রুচিরার কাছে এসে, নম্রভাবে ওর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলো। সারা ঘর নিশ্চুপ ... কয়েক মুহূর্ত সময় নিলো, হাসির বোমাটা ফাটতে। তারপর হাসির অট্টরোল। এর মধ্যেই সদা সপ্রতিভ ললিত বোকা মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। ভাবছে গোলমালটা কোথায়?সুমিত্রা হাসি সামলে বললো, ‘‘ললিত ও তো আমার বন্ধু রুচিরা। যার বিয়ের পরে তুমি গলায় দড়ি দেবে ঠিক করেছিলে। চিনতে পারলে না তো?’’আবার হাসির ঝর্ণা – সে হাসি আর থামতেই চায় না। ললিত আস্তে আস্তে ঘর ছেড়ে লাগোয়া বারান্দায় চলে গেলো, মনে পড়ে গেলো সব পুরোনো কথা। এই বোকা বোকা কাণ্ডটা কিভাবে যে সামাল দেবে ভেবে পাচ্ছে না।এবার এইসব আনন্দিত মহিলারা আড্ডা শেষ করে উঠতে শুরু করলো। বিদায় পর্বে যথারীতি আবার দেখা হবার প্রতিশ্রুতি। বারান্দা পার হয়ে সবাই পাঁচধাপ সিঁড়ি দিয়ে রাস্তায় নেমে আসছে। সব শেষে আসছিলো রুচিরা। বারান্দার গ্রীল ধরে দাঁড়িয়ে থাকা উদাস ললিত এবার এগিয়ে এলো ‘‘রুচিরা, আমি কিন্তু আজও তোমায় ভালোবাসি। তোমার মোবাইল নাম্বারটা আমাকে দেবে?’’ কথাটা সবার কানেই গেলো – সবাই স্তম্ভিত। হাসির ঝর্ণাটা শুকিয়ে গেছে মনে হচ্ছে। কারো মুখে কোন কথা নেই। একটা রূদ্ধশ্বাস পরিবেশ। এর মধ্যে দমকা ঝোড়ো বাতাসের মতো এক সুন্দরী নারীর প্রবেশ। বাজখাঁই কণ্ঠস্বর সপ্তমে – ‘‘আচ্ছা, তুমি তাহলে এখানে – সুযোগ পেয়েই একপাল মহিলার মধ্যে সেঁটে গেছো। বাড়ী চলো।’’ ললিত একবার রুচিরার দিকে কাতর চোখে তাকিয়ে, বউ এর পেছন পেছন প্রস্থান। মহিলারা সবাই একটু মুচকি হাসলো। - সবিতা সেন২০.০৫.২০২৪নতুন উদ্দীপনা - Sobuj Chatterjee | কাঁটাতারে কি সেতার তৈরী হয়সঙ্গীত এক ছন্দোবদ্ধ কোলাহল সাম্যের আধারে জীবন অকুতোভয় মৌন পাহাড়ে বেজে উঠছে দৃপ্ত মাদল। পরতে পরতে জীবন রয়েছে জীবনেতবু সমনে বেসুরো অভিপ্রায়সাথীদের রাগ সুস্থ পরিবর্তনেহয়তো শুরু নতুন উদ্দীপনায়। কুশীলব গেলে মঞ্চ কি খালি হয়অনেক তারা আলো নিয়ে আসতে পারেব্রহ্মান্ডের উৎসবে জড়াবে হৃদয় মেঘেরা সব জড়ো হচ্ছে বৈতরণীর পাড়ে। আবার লাবণ্যে ভরপুর হবে ধরাপ্রতি বিন্দুতে ভালোবাসার প্রতিশ্রুতিএই লগ্নে বিলুপ্ত হোক খরাঅশ্রু মদিরায় সিক্ত যাপনের সম্মতি ।।
ভাট...
 অরিত্র | আমাদের বাড়িতে বিজেপির ম্যানিফেস্টো বা ভোটার স্লিপও আসেনি। শুধু সিপিএম আর তৃণমূলের দিয়ে গেছিল।
অরিত্র | আমাদের বাড়িতে বিজেপির ম্যানিফেস্টো বা ভোটার স্লিপও আসেনি। শুধু সিপিএম আর তৃণমূলের দিয়ে গেছিল। অরিত্র | আমাদের কলকাতা দক্ষিণ তো বটেই, কলকাতা উত্তর, যাদবপুর ও ডায়মন্ড হারবার পুরোটাই তৃণমূলকে ছেড়েছে বিজেপি। ডায়মন্ড হারবারে শুনলাম মাস স্কেলে ছাপ্পা হয়েছে। আমাদের কলকাতা দক্ষিণে বিজেপির কোনো প্রচারই দেখলাম না, আমাদের এরিয়াতে রাস্তায় বিজেপির একটা ফ্ল্যাগও বা পোস্টারও ছিল না। অথচ এইসব এলাকা অবাঙালি পপুলেশন আছে বলে বিজেপির প্রকৃত সমর্থক ভিত্তি আছে। এই চারটের একটাতেও বিজেপি জেতার কাছাকাছিও গেলে খুবই অবাক হব। উত্তর কলকাতা ছাড়া অন্যগুলোতে বিজেপি সম্ভবত তৃতীয় হওয়া ঠিক করেছে। দেখা যাক।
অরিত্র | আমাদের কলকাতা দক্ষিণ তো বটেই, কলকাতা উত্তর, যাদবপুর ও ডায়মন্ড হারবার পুরোটাই তৃণমূলকে ছেড়েছে বিজেপি। ডায়মন্ড হারবারে শুনলাম মাস স্কেলে ছাপ্পা হয়েছে। আমাদের কলকাতা দক্ষিণে বিজেপির কোনো প্রচারই দেখলাম না, আমাদের এরিয়াতে রাস্তায় বিজেপির একটা ফ্ল্যাগও বা পোস্টারও ছিল না। অথচ এইসব এলাকা অবাঙালি পপুলেশন আছে বলে বিজেপির প্রকৃত সমর্থক ভিত্তি আছে। এই চারটের একটাতেও বিজেপি জেতার কাছাকাছিও গেলে খুবই অবাক হব। উত্তর কলকাতা ছাড়া অন্যগুলোতে বিজেপি সম্ভবত তৃতীয় হওয়া ঠিক করেছে। দেখা যাক। b | ইন্ডিয়ান এক্স্প্রেসে লিখেছে ঃগতবার ১৩ খানা এক্সিট পোলের গড় নিয়ে প্রেডিকশন ছিলো এন ডি এ ৩০৭ আর ইউ পি এ ১২০ না কতো . গতোবার এন ডি এ পেয়েছিলো ৩৫৩ আর ইউ পি এ ৯৪।
b | ইন্ডিয়ান এক্স্প্রেসে লিখেছে ঃগতবার ১৩ খানা এক্সিট পোলের গড় নিয়ে প্রেডিকশন ছিলো এন ডি এ ৩০৭ আর ইউ পি এ ১২০ না কতো . গতোবার এন ডি এ পেয়েছিলো ৩৫৩ আর ইউ পি এ ৯৪।
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাবিপ্লবের আগুন - পর্ব সাত - কিশোর ঘোষাল
০১ জুন ২০২৪ | ৩৯ বার পঠিতপরের দিন খুব ভোরবেলাতেই ভল্লার ঘুম ভেঙে গেল। আজ বেশ সুস্থ বোধ করছে সে। শরীরের ব্যথা, বেদনা – গ্লানি নেই বললেই চলে। বিছানায় উঠে বসল, তারপর ধীরে ধীরে ঘরের বাইরে এল। ভোরের আলো সবে ফুটেছে, বাইরের গাছপালার ডালে ডালে পাখিদের ব্যস্ততা টের পাওয়া যাচ্ছে তাদের কলকাকলিতে। হাওয়ায় সামান্য শিরশিরে ভাব। বিছানায় ফিরে গিয়ে সে গায়ের চাদরটা তুলে নিয়ে গায়ে জড়াল। দড়ি থেকে টেনে নিল গামছাটা – কষে বেঁধে নিল মাথায়। তারপর...
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালস্মৃতির রাজ্য শুধুই শ্লোগানময়-২ - প্রবুদ্ধ বাগচী
০১ জুন ২০২৪ | ৪৩ বার পঠিতবিগত চার দশকের রাজনৈতিক স্লোগান ও দেওয়াললিখন
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজারাবণের প্রার্থনা - তাতিন
০১ জুন ২০২৪ | ১৩৬ বার পঠিত... কোথায় গেল আজ সূর্যতিলক আর কোথায় ফার বনে মরেছে কাক নবমীমিছিলের অস্ত্র ঝনঝনে পকেটে গেল না কি পনেরো লাখ?...
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালভোটুৎসবে ভাট - হযপচো - সমরেশ মুখার্জী
০১ জুন ২০২৪ | ৬৭ বার পঠিতহঠাৎ কোনো প্রসঙ্গে মাথা চুলকে ওঠে। তা নিয়ে রম্যরচনা জাতীয় কিছু লিখে ফেলি। তবে সেসব রসে রম্য বা আঙ্গিকে রচনা পদবাচ্য হয় কিনা জানিনা। ভার্চুয়াল ডায়েরিতে দেখি এই ডিজিটাল ডায়েরিয়াটি লিখেছিলাম আজ থেকে ঠিক চার বছর আগে - ১লা জুন ২০২০. তখন ছিলাম মনিপাল, কর্ণাটকে। তবে এটার মূল প্রতিপাদ্য আজও রিলেভ্যান্ট। ভবিষ্যতেও থাকবে
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাকাদামাটির হাফলাইফ - ইট পাথরের জীবন - ইমানুল হক
০১ জুন ২০২৪ | ৪৫ বার পঠিতআর কয়েকটা পরিবর্তন হয়েছে। ফুটবল খেলার মাঠে লোক নেই। সেখানে কিছুটা ঘিরে ঈদগাহ তলা। বেনে পাড়া বামুনপাড়ায় খেলার জায়গা ছিল না। দুটি পরিবার হাওড়া প্রবাসী হওয়ায় জায়গা মেলে। ছোটখাটো খেলার মাঠ হতেই পারতো। সেখানে এখন বড় দুর্গামন্দির। শিবমন্দির ছিল আগে মাটির। এখন শিব আর ওলাইচণ্ডীর আলাদা ঘর হয়েছে। আগে দুর্গাও ওখানে আসতেন। শিব লিঙ্গ সারা বছর থাকে। ওলাইচণ্ডীর বিসর্জন হয়। দুর্গারও। তবু আলাদা দুটি মন্দির।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালবৈঠকি আড্ডায় ১৭ - হীরেন সিংহরায়
০১ জুন ২০২৪ | ২২২ বার পঠিতসকাল থেকে অন্ধকার হয়ে আছে আকাশ। কে বলবে এটা মে মাস ? বুথের ভেতরে ছ জন কর্মী , হলে আমরা চারজন । শুধু ভোটার কম পড়িয়াছে ! অনেকদিন আগে দেশে দেখা একটা ছবি মনে পড়ে গেল – আই এস জোহরের একটা কলাম ছিল ফিল্ম ফেয়ারে , তাতে কার্টুন :ফার্স্ট ক্লাস কামরায় একজন যাত্রী বসে আছেন তাঁকে ঘিরে কন্ডাক্টর , চা ওলা সহ আরও কয়েকজন । নিচে মন্তব্য - উই অলওয়েজ হ্যাভ মোর পিপল সারভিং ওয়ান কাসটমার !সারা দেশের ভোট গণনা শেষ হতে সকাল। প্রিসাইডিঙ অফিসার একেক বার মাইক দখল করে ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড ফলাফল ঘোষণা করেন । দশটি আসনের ন’টিতে লিব ডেম বিজয়ী। সবচেয়ে বড়ো সাফল্য- বারো বছরের সিটিং কাউন্সিলর ন্যাপহিলের পোস্ট মাষ্টার সাজ হুসেনকে হারালেন স্থানীয় রাজনীতিতে সম্পূর্ণ নতুন চেহারা জন পিয়ারস । তিনি ও আমি একত্রে জন গণেশের দুয়ার প্রদক্ষিণ করেছি কিন্তু ভাবতে পারি নি ষাট পেরুনো এক রিটায়ার্ড আই টি এঞ্জিনিয়ার সমাজে পরিচিত মুখ এক পোস্ট মাষ্টারকে দুশো ভোটের ব্যবধানে তাঁর আসন থেকে সরাতে পারবেন ! বোধহয় লেবার প্রধান মন্ত্রী হ্যারলড উইলসন বলেছিলেন, এ উইক ইজ এ লং টাইম ইন পলিটিক্স।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালভিকারুন্নেসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ! - Muhammad Sadequzzaman Sharif
০১ জুন ২০২৪ | ১১৩ বার পঠিতমাউশির আইন আর ভিকারুন্নেসার আইন আলাদা! মাউশি যে বয়স সীমা দিয়েছে তার সাথে ভিকারুন্নেসার বয়স সীমার পার্থক্য আছে! এইটা অনেক অনেক অভিভাবকই জানে না। কেউ জানলেও মাউশি যেহেতু আবেদন করতে দিয়েছে দেখি আবেদন করে। আইনে না হলে বাতিল হয়েই যাবে, সমস্যা কী? সমস্যা হল ভিকারুন্নেসা তাদের আলাদা বয়স সীমা মাউশিকে জানায় নাই, নিজেরাও কোন উদ্যোগ নেয় নাই। ফলাফল? ১৬৯ জন শিশুর সুযোগ হয়ে গেছে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির! এরপরেও যদি দুই পক্ষ এইটার সমাধানের চেষ্টা করত তবুও বছরের মাঝে এসে এমন বিপদ তৈরি হত না এই ফুলের মতো শিশু গুলোর। লটারিতে টিকলেই তো হল না, বাচ্চার কাগজ পত্র সব ঠিক আছে কি না এগুলা যাচাই বাছাইয়ের ব্যাপার আছে না? ভিকারুন্নেসা এই যাচাই বাছাইয়ের কাজও সফল ভাবে করেছে। তখনও বাদ দেয় নাই এদেরকে! তখন বাদ দিলে এই অভিভাবকেরা একটু ঘাইঘুই করে মেনে নিত হয়ত। ভিকারুন্নেসা যুক্তি দেখাতে পারত যে আমাদের এখানে এই বয়স সীমা, এর বাহিরে আমরা নিব না। কিন্তু তা হয়নি। এদেরকে ভর্তি করা হয়েছে। বাচ্চারা ক্লাসও শুরু করেছে। ভিকারুন্নেসা তখন কেন এইটা করতে পারে নাই? তখন মহামান্য মাউশি ধমক দিয়ে বলেছিল তাদের আইনই আইন, এর বাহিরে কেউ আলাদা করে ভর্তির জন্য নতুন আইন তৈরি করতে পারবে না। আমার বন্ধু নিজে মাউশিতে গিয়েছিল, ওকেও মৌখিক ভাবে বলে দেয় যে সোজা ভর্তি করায় ফেলেন, আমরা যা বলছি ওইটাই ঠিক!
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালএক ‘নিউ বাংলাদেশ’ এর কথা - মোহাম্মদ কাজী মামুন
০১ জুন ২০২৪ | ৯৫ বার পঠিতখবরে প্রকাশ, রাজধানী ঢাকার সৌন্দর্য পরিবর্ধনে বেশ কিছু প্রকল্প হাতে নিয়েছে ঢাকা দক্ষিন সিটি কর্পোরেশান। এর মধ্যে একটি প্রজেক্ট ১৯১৯ কোটি টাকার। যার আওতায় রয়েছে খেলার মাঠ, কমিউনিটি সেন্টার, পুকুর আধুনিকায়নের পরিকল্পনা, যার বাস্তবায়ন দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। এছাড়া কালুনগর, জিরানি, মান্দা ও শ্যামপুরে খাল নির্মাণেও অনুষ্ঠিত হচ্ছে ব্যাপক কর্মযজ্ঞ; সীমানপ্রাচীর, যানবাহন ও পথচারী চলার জন্য সেতু, পায়ে চলার পথ, পাবলিক টয়লেট, প্লাজা, সাইকেল লেন, আর বৈদ্যুতিক বাতির থাম – সব কিছু দাঁড়িয়ে যাচ্ছে ছায়াছবির মত। একই সাথে অনেক কিছু উধাও হচ্ছেও ছায়াছবির মত; যেমনঃ পুকুর বা খালের উন্নয়নে টনকে টন কংক্রিট গেলে দেয়া হচ্ছে পার্শ্ববর্তী সব সবুজকে উচ্ছেদ করে!
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজা'মোদী কি গ্যারান্টি': বিজ্ঞাপনতন্ত্রের এক নয়া রাজনৈতিক প্রয়োগ - অত্রি ভট্টাচার্য
৩১ মে ২০২৪ | ২১৯ বার পঠিত'নিও-লেফট' বামপন্থার তাত্ত্বিক রেমন্ড উইলিয়ামস, তার বহুপঠিত 'অ্যাডভার্টাইজিং: দ্য ম্যাজিক সিস্টেম' নিবন্ধে দেখিয়েছিলেন, কিভাবে সমাজপরিমন্ডলের ব্যক্তিমানুষ পুঁজিতন্ত্রের দৌলতে 'বিষয়' হয়ে ওঠে, হয়ে ওঠে 'নির্বাচক'মাত্র এবং স্বয়ম্ভূ 'জনতা'র সার্বভৌম অবস্থান থেকে সে হয়ে ওঠে 'জনমত' নামক একরৈখিক, সমসত্ত্ব কন্ঠস্বর। সিদ্ধান্ত গ্রহণ গণতন্ত্রের একটি ফাংশনে' পর্যবসিত হয়, কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রণোদনা জোগানোর জন্য একটি নতুন ব্যবস্থা কায়েম করা হয়, যাতে করে সংখ্যাগরিষ্ঠকে একটি বিশেষ শাসনকাঠামো নির্মাণের লক্ষ্যে সংগঠিত করা যায়, তৈরি করে নেওয়া যায় নিজেদের প্রয়োজনীয় 'জনমত'। এই ব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠকে জনপিন্ড হিসাবে দেখা হয়, যাদের মতামত, জনসমূহ হিসাবে গৃহীত হবে, ব্যক্তি হিসাবে নয়, এই রূপান্তর 'বিজনেস অফ গভর্নেন্সের' একটি জরুরী ফ্যাক্টর। ব্যবহারিক পরিপ্রেক্ষিতে, এই রাজনীতি, বৃহৎ-পুঁজি, আমলাতন্ত্র ও বিজ্ঞাপনীজগতের মিলিঝুলি জাদুকাঠামো দীর্ঘ সময়ের জন্য সফলও হতে পারে, কিন্তু সামাজিক সমস্যাগুলি বর্ণনা করা ক্রমশ কঠিন হয়ে ওঠে, যেহেতু প্রচারকের পেশা এবং প্রচারকের বাস্তবতার ব্যবধান রয়েছে। অধিকন্তু, শাসক একটি অত্যাধুনিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় প্রকৃত ক্ষমতার জন্য ক্রমবর্ধমানভাবে আগ্রাসী ভূমিকা নেওয়ার ফলে, পুরানো সামাজিক-রাজনৈতিক প্রশ্নগুলি অপ্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে এবং, নয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণ সমস্ত সামাজিক কার্যকলাপের মূল উদ্দেশ্য হয়ে ওঠে।
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাবাংলায় বামের ভোট কি বাড়বে? - উপল মুখোপাধ্যায়
৩১ মে ২০২৪ | ৩০৯ বার পঠিতমন চায় বামের ভোট বাড়ুক। কিন্তু নরেন্দ্র মোদির ভারতে সম্ভবনার শিল্পে কি সে লেভেল প্লেয়িং গ্রাউন্ড আছে যেখানে বামেরা খেলতে পারে ? স্বতন্ত্র শক্তি হিসেবে বামেদের ভূমিকা এমনকি এই বাইপোলার পরিস্থিতিতেও অনস্বীকার্য। তাই তাদের ভোট দেওয়াটাও গুরুত্বপূর্ণ। খেলার ছলে কেই বা নেবে কৃষক আন্দোলনের অন্যতম চালিকা শক্তি বামেদের? মুশকিল হল ২০২৪ য়ের সাধারণ নির্বাচনে বামেদের বড় অংশকে বেশির ভাগ আসনেই ইন্ডিয়া জোটের আঁতাতের বাইরে প্রার্থী দিতে দেখা গেছে। সবচেয়ে বড় বাম দল সি পি আই এম দিয়েছে মোট বাহান্নটা আসনে। তার মধ্যে কেরালার পনেরোটা সিটে আর বাংলার তেইশটা যথাক্রমে কংগ্রেস আর তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। ইন্ডিয়া জোটের নেতৃত্ব এই শরিকি লড়াইয়ে ভাবিত নয় কারণ এই দু রাজ্যে জোট করতে যাওয়ার বাস্তবতা নেই। উল্টে করতে গেলে বিরোধী স্পেস বিজেপি খেয়ে নিতে পারে। এ কথাটা কেরালা আর পশ্চিম বাংলা এই দু রাজ্যে শুধু নয় পাঞ্জাবের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সেখানেও রাজ্যে ক্ষমতায় থাকা আপ আর কংগ্রেসের মধ্যে দা কাটারি সম্পর্ক। অর্থাৎ যেখানে নির্বাচনী জোট হয়নি সেখানে নির্বাচন পরবর্তী জোটের কথাই ইন্ডিয়া জোটের নেতৃত্বের মাথায় আছে। সে কথা মাথায় রেখে, পশ্চিম বঙ্গে দুই যুযুধান ইন্ডিয়া শরিক তৃণমূল কংগ্রেস আর বামফ্রন্ট-কংগ্রেস ভোট পরবর্তী অবস্থান নিয়ে এখনই বিতর্কে মেতেছে। উদ্দেশ্য নিজের নিজের ভোট ব্যাংক চাঙ্গা রাখা।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালদোলজ্যোৎস্নায় শুশুনিয়ায় - ১৫ - সমরেশ মুখার্জী
৩১ মে ২০২৪ | ৩৭ বার পঠিতআশির দশকে যাদবপুরের কয়েকটি ছাত্রছাত্রী শুশুনিয়া পাহাড়ে গেছে শৈলারোহণ অভ্যাস করতে - সেই ভিত্তিতে এই আখ্যান … অমিয়দা বললেন, "কী বলতে চাইছি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো। ক্লাইম্বিং জগতে ওনারা মহাপুরুষ। নমস্য ব্যতিক্রম। অনেকেই পাহাড়ে দূর্ঘটনায় অকালে প্রয়াত। আমরা সাধারণ মানুষ। তাই চলবো সুরক্ষা নিয়ম মেনে। কী মনে থাকবে, তো?" শৈলারোহণ যে মোটেও ছেলেখেলার বিষয় নয় তা অমিয়দা দুটো বাস্তব উদাহরণ দিয়ে প্রাঞ্জল ভাবে বুঝিয়ে দিলেন …
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালকিষেণজি মৃত্যু রহস্য - পর্ব ১১ - বিতনু চট্টোপাধ্যায়
৩১ মে ২০২৪ | ৮৬ বার পঠিতসেদিন ছিল ২০০২ সালের ২৬ অক্টোবর। একদম সকাল সকাল একটা খুন হল জামবনির জামুই গ্রামে। দিবাকর মালাকার নামে এক স্থানীয় সিপিআইএম নেতা তাঁর দুই সঙ্গী মানিক শতপথী এবং হেনা শতপথীর সঙ্গে মোটরসাইকেলে চেপে যাচ্ছিলেন। সকাল সাতটা-সাড়ে সাতটা হবে। দিবাকর মালাকার ছিলেন বাসু ভকতের অনুগামী এবং এলাকায় যথেষ্ট প্রভাবশালী নেতা। অত সকালে আক্রমণ হতে পারে ভাবতে পারেননি। খুব কাছ থেকে দিবাকর মালাকারকে গুলি করা হয়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হল দিবাকর মালাকারের।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালভোটুৎসবে ভাট - মক্ষী দর্পণ - সমরেশ মুখার্জী
৩০ মে ২০২৪ | ৭৮ বার পঠিতশিরোনাম দেখে মনে হতে পারে লেখাটি “নীল দর্পণ” দ্বারা অনুপ্রাণিত। কিন্তু মক্ষী দর্পণে কোনো জ্বলন্ত আর্থসামাজিক বিষয়ে আলোচনা করা হয়নি। সে যোগ্যতাও আমার নেই। এটা ভোটের বাজারের হুল্লোড়ে পরিবেশিত একটি পাতি রম্যরচনা। এই ডিসক্লেমার সত্ত্বেও যদি কেউ লেখাটি পড়েন এবং বিরক্তির উদ্রেক হয় অনুগ্ৰহ করে আমায় গাল দেবেন না
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালসত্যজিৎ এবং কিশোরকুমার - সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায়
৩০ মে ২০২৪ | ১৩৪ বার পঠিতসত্যজিৎ ঘরে-বাইরেতে সন্দীপের গলায় কিশোরকুমারকে গিয়ে গান গাইয়েছিলেন। কেন গাইয়েছিলেন? আপনারা সক্কলেই ঘরে-বাইরে পড়েছেন। ফলে আলাদা করে বলার কিছু নেই, রবীন্দ্রনাথের দুখানা উপন্যাস খুবই প্রচারধর্মী, গোরা এবং ঘরে-বাইরে। গোরাতে প্রায় চোঙা ফুঁকে ভালো-ভালো কথা বলা হয়েছে। ঘরে-বাইরেতে অতটা নয়। কিন্তু তাতেও, সেটা প্রায় কুরুক্ষেত্র। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং নিখিলেশ হয়ে সন্দীপকে শৈল্পিক কথার মারপ্যাঁচে নানা ব্রহ্মাস্ত্র ঝেড়েছেন। বিমলা বেচারি সেই যুদ্ধক্ষেত্রে প্রায় উলুখাগড়া। তাকে বাদ দিলে ওটা আর উপন্যাস না হয়ে 'স্বদেশী বিষয়ক আবর্তক ও নিবর্তক সম্বাদ' হয়ে যেত, তাই রাখা।
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাআইটির ভাইটি - কণিষ্ক
৩০ মে ২০২৪ | ৭৮০ বার পঠিতআজকের যুগে দাঁড়িয়ে যেখানে তরুণ থেকে বয়স্ক সবাই নিয়মিত ইন্টারনেটে আনাগোনায় স্বচ্ছন্দ সেখানে নিজেদের সম্ভাব্য ভোটারকে টার্গেট করতে সমস্ত রাজনৈতিক দলই নিজেদের আইটি সেল তৈরি করে ফেলেছে। কারও আইটি সেল বেশি সক্রিয়, কারও কম, তবে প্রত্যেকেই অঞ্চল বুঝে, অডিয়েন্স বুঝে, কোন মাধ্যমে বলা হচ্ছে তার ওপর ভিত্তি করে ভিন্ন ভিন্ন ধরণের প্রচার কৌশল নিয়ে থাকে। কিন্তু কোনো কোনো রাজনৈতিক দলের আইটি সেল অনেক আগেই তাদের কার্যকলাপ শুরু করায় সেই পরিমাণ সাফল্য পেতে বা ততটা নেটওয়ার্ক তৈরি করতে বাকিদের আরোও বেশি কাঠখড় পোড়াতে হবে।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালমহাকাশের আলো - অনির্বাণ কুণ্ডু
৩০ মে ২০২৪ | ২৫৮ বার পঠিত১৯৪৮ সালে র্যালফ আলফার ও রবার্ট হারম্যান দেখালেন, যে, গ্যামোর তত্ত্ব যদি সত্যি হয়, তাহলে সেই মহাবিস্ফোরণের কিছু অনুরণন এখনো খুঁজে পাওয়া উচিত। শক্তি বা তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গের ক্ষেত্রে এই অনুরণনটা হবে কৃষ্ণবস্তু বিকিরণ, যার উষ্ণতাও তাঁরা হিসেব করলেন, মান বেরোলো ৫ কেলভিনের মতন। ৫ কেলভিন মানে ‘–২৬৮° সেলসিয়াস’, অর্থাৎ মহাকাশ খুবই ঠান্ডা জায়গা। কিন্তু মহাবিশ্ব বরাবর এমন ঠান্ডা ছিল না। বিগ ব্যাং তত্ত্ব বলে, অতীতে মহাবিশ্বের আয়তন যখন খুব ছোটো ছিল, তখনো এই অনুরণনটা কৃষ্ণবস্তু বিকিরণই ছিল, কিন্তু তার তরঙ্গদৈর্ঘ্য ছিল অনেক কম, অর্থাৎ এক একটা ফোটনের শক্তি ছিল অনেক বেশি। যত দিন গেছে, এই বিকিরণ ঠান্ডা হয়ে এসেছে। অর্থাৎ, এই বিকিরণ খুঁজে পাওয়া গেলে আর উষ্ণতা হিসেবের সঙ্গে মিলে গেলে তা ‘বিগ ব্যাং’ তত্ত্বের পক্ষে অকাট্য প্রমাণ হবে।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালতোমার বাস কোথা যে... - ৪ - Nirmalya Nag
৩০ মে ২০২৪ | ২৩২ বার পঠিত“অরুণাভ দাস। আপনাদের তো দেখেছি, গত মাসে মিস্টার শর্মার ছেলের বার্থডে পার্টিতে। গেছিলেন না?” পরিস্কার বাংলায় বলল ডাক্তার। “হ্যাঁ, কিন্তু…,” অরুণাভর কথা শেষ হল না, ইন্দ্রনীল হাত তুলে তাকে থামাল। “আপনার শার্ট, টাই আর স্যুট ছিল ডিফরেন্ট শেডস অফ ব্লু। আর ম্যাডাম,” বিনীতার দিকে তাকাল সে, “আপনি পরেছিলেন একটা লাল গর্জাস শাড়ি।” “বাব্বা, আপনি তো দারুণ লোক। গত মাসে পার্টিতে একবার দেখলেন, আর তাদের ড্রেস, শাড়ি সব মনে করে রাখলেন,” বলল অরুণাভ। “শুধু শাড়ি না, আরো অনেক কিছু বলতে পারি।” “মানে?” ভ্রূ কুঁচকে গেল বিনীতার।
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাপশ্চিমবঙ্গ - ফলাফল কী হতে চলেছে - সঞ্জয় সরকার
২৯ মে ২০২৪ | ৬৩১ বার পঠিতলোকসভা ভোট শেষ দফায়। এবার ভোটে উত্তুঙ্গ কোনো উদ্দীপনা ছিলনা, ছিলনা কোনো হাওয়া, চাপা এক উৎকণ্ঠা নিয়ে ভোট হয়েছে। সেই ধারা শেষ দফায়ও অব্যাহত। রাজনৈতিক পটচিত্রে উত্তেজনার অবশ্য কোনো অভাব হয়নি। অভাব হয়নি নাটকীয়তার। ভোটের ঠিক আগে নির্বাচনী বন্ড সংক্রান্ত রায় এসেছে সুপ্রিম কোর্টের। নির্বাচনের মধ্যেই এসেছে কলকাতা হাইকোর্টের পরপর দুটি রায়। একটিতে বিপুল সংখ্যক রাজ্য সরকারি শিক্ষককে কর্মচ্যুত করা হয়েছে, অন্যটিতে ২০১০ সালের পর পশ্চাদপদ অংশের সংরক্ষণকে একরকম করে বাতিল করা হয়েছে। দুটির চূড়ান্ত রায়ই অবশ্য সুপ্রিম কোর্টে ঝুলে। সন্দেশখালি ভোটের আগে থেকেই শিরোনামে। কিন্তু ভোটের মধ্যে এসেছে নতুন চমক। গঙ্গাধর কয়ালের এবং আরও কয়েকটি ভিডিও ফাঁস হয়ে ভাইরাল। এসেছে স্বয়ং রাজ্যপালের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থার অভিযোগ।
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাপায়েল কাপাডিয়ার ছবি, ভালোবাসা, বন্ধুত্ব ও রাজনীতি - সোমনাথ গুহ
২৯ মে ২০২৪ | ২৫৩ বার পঠিতপায়েল কাপাডিয়ার ছবিতেও এই রাজনৈতিক সচেতনতার আভাস পাওয়া যায়। তাঁর ছবির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল রাজনীতি আর ব্যক্তিগত জীবন সমান্তরাল ভাবে চলে, এমনও মনে হতে পারে যেন দুটো ভিন্ন কাহিনি। রাজনীতি বলতে দলীয় মিটিং, মিছিল নয়, কোন ইস্যু, বিক্ষোভ, প্রতিবাদকে পূর্বনির্ধারিত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখা নয়, নির্মোহ ভাবে বৃহত্তর ও ব্যক্তিগত পরিসর কে ফুটিয়ে তোলা। পায়েল আগেও কান উৎসবে অংশগ্রহণ করেছেন, পুরষ্কার জিতেছেন। ২০১৭ সালে তাঁর ‘আফটারনুন ক্লাউডস’ একমাত্র ভারতীয় ছবি যা উৎসবে নির্বাচিত হয়েছিল। ২০২১ সালে তাঁর তথ্যচিত্র ‘আ নাইট অফ নোইং নাথিং’ সেরা ডকুমেন্টারি ছবির জন্য ‘গোল্ডেন আই’ পুরষ্কার পায়। এই ছবিতে ২০১৫ সালে FTII এ মহাভারত-খ্যাত গজেন্দ্র চৌহানকে প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ করার প্রতিবাদে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল তা দেখান হয়েছে। প্রসঙ্গত পরিচালক নিজে এই আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন যার জন্য তিনি প্রায় সাড়ে চার মাস ক্লাস বয়কট করেছিলেন এবং তাঁর অনুদানও বন্ধ হয়ে গেছিল। ছাত্রদের এই প্রতিবাদ দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছড়িয়ে পড়ে। এরই মধ্যে এক কলেজের ছাত্রী তার প্রেমিকের অনুপস্থিতি অনুভব করছে। একই চিঠিতে সে লিখছে ক্যাম্পাসে কী হচ্ছে সে বুঝে উঠতে পারছে না, হয়তো স্ট্রাইক করার জন্য তাঁদের শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। মুসলিম যুবককে চোখ বেঁধে, কোমরে পিস্তল ঠেকিয়ে পুলিশের জিপে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, একই সাথে মেয়েটি চিঠিতে তার চারিপাশের বাস্তব, কল্পনা, স্বপ্ন, ফ্যান্টাসি উজাড় করে দিচ্ছে। এই ভাবে পরিচালক পলিটিকাল আর পারসোনালের মধ্যে আন্তসম্পর্ক খুঁজছেন, বোঝার চেষ্টা করছেন।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালদোলজ্যোৎস্নায় শুশুনিয়ায় - ১৪ - সমরেশ মুখার্জী
২৯ মে ২০২৪ | ৬৮ বার পঠিতআশির দশকে যাদবপুরের কয়েকটি ছাত্রছাত্রী শুশুনিয়া পাহাড়ে গেছে শৈলারোহণ অভ্যাস করতে - সেই ভিত্তিতে এই আখ্যান … অমিয়দা বললেন, "আমি তোমাদের রক ক্লাইম্বিং কোর্সে যাইনি। তাই এখন সরাসরি পাথরে গিয়ে চড়ার আগে শৈলারোহণের যে কিছু নিয়মকানুন আছে, যা তোমরা কোর্সে শিখেছো সেগুলো একটু ঝালিয়ে নেওয়া যাক। তোমরা হয়তো জানো শৈলারোহণ ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল ইওরোপে, বলা ভালো মূলতঃ ব্রিটেনে। তাই এখোনো বহু দেশে ব্রিটিশ মাউন্টেনিয়ারিং কাউন্সিল বা BMC প্রবর্তিত ক্লাইম্বিং টেকনিক, প্রোটোকল, সুরক্ষা নিয়ম, ইকুইপমেন্ট স্পেসিফিকেশন ইত্যাদি গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে বিবেচিত হয়। তার কারণ ব্রিটিশরা খুব মেথডিক্যাল।" …
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজানরেন্দ্র মোদীর গুজরাট মডেল - দ্বিতীয় পর্ব - প্রদীপ দত্ত
২৮ মে ২০২৪ | ৭০৯ বার পঠিতসেন্টার ফর মনিটরিং ইন্ডিয়ান ইকোনমির (সিএমআইই) তথ্য দেখায় যে, ২০০৩ সাল থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত, গুজরাটে এই ধরনের বিনিয়োগকারী সম্মেলনগুলিতে দেওয়া প্রতিশ্রুতির মাত্র ২৫ শতাংশ দিনের আলো দেখেছিল৷ অনেক বিজেপি শাসিত রাজ্য একে মডেল হিসাবে গ্রহণ করেছে। যেমন -- হ্যাপেনিং হরিয়ানা, মোমেন্টাম ঝাড়খণ্ড, রিসার্জেন্ট রাজস্থান ইত্যাদি। উত্তরপ্রদেশ (ইউপি ইনভেস্টর সামিট), পশ্চিমবঙ্গ (বেঙ্গল গ্লোবাল সামিট), ঝাড়খন্ড এবং ওড়িশাও বিনিয়োগের উপযুক্ত গন্তব্য হিসাবে নিজেকে তুলে ধরার জন্য ভাইব্রেন্ট গুজরাট সামিটের অনুরূপ সংস্করণ আয়োজন করেছে। কিন্তু সব জায়গাতেই একই কান্ড– বড় বড় ঘোষণার কিছুকাল পর দেখানোর মতো কিছু নেই। ইভেন্টের সময় যে মৌ (এমওইউ) স্বাক্ষরিত হয়, খুব কমই প্রকৃত বিনিয়োগ হয়, কারণ মৌগুলির কোনও আইনি বাধ্যবাধকতা নেই। এই জাতীয় শোগুলির পর বলার মতো কর্মসংস্থান যে হয় এমন কোনও বিশ্বাসযোগ্য তথ্যও নেই।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালভোটুৎসবে ভাট - স্বপনে তাহারে (পুনশ্চ) - সমরেশ মুখার্জী
২৮ মে ২০২৪ | ৭৭ বার পঠিতআগে মাঝেমধ্যে টুকটাক ঢুকলেও গুরুতে প্রথম মজলুম ২৮.১০.১৮ সন্ধ্যায়। সেদিন ২৪.৭.১৪তে শিবাংশু লিখিত “আমাকে তুই আনলি কেন…” চোখ পড়লো। খানিকটা পড়েই জমে গেলাম। অতঃপর অনেক রাত অবধি ২১ পর্বের ১১ হাজার শব্দেরও বেশী সেই লেখা একলপ্তে পড়ে শেষ করলাম। শুধু তাই নয়, মাঝে মাঝে থাকতে না পেরে, তার কিছু কিছু ভালো লাগা অংশ কপি করে হোয়াতে পেষ্ট করে মুষ্টিমেয় কজন বন্ধু এবং এক প্রাচীন বান্ধবীকেও পাঠিয়েছি। শিবাংশু গুরুতে (আপাতত) শেষ লেখাটি লেখেন ২০.৩.২১ - “স্বপনে তাহারে” - বিখ্যাত ডিডেকটিভ গল্প লেখক স্বপনকুমার প্রসঙ্গে। বর্তমান খাজা রচনাটি সেটি হতে অনুপ্রাণিত
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজানরেন্দ্র মোদীর গুজরাট মডেল - প্রথম পর্ব - প্রদীপ দত্ত
২৭ মে ২০২৪ | ১১০০ বার পঠিতগুজরাত দাঙ্গার সময় রাস্তায় উন্মত্ত হিন্দু গোষ্ঠীর লোকেরা শুধু স্থানীয় মুসলমানদেরই হত্যা করেনি, এক হাজারের বেশি ট্রাকও জ্বালিয়ে দিয়েছিল। জেনারেল মোটরস কারখানায় তৈরি জাহাজে পাঠানো ‘ওপেল অ্যাস্ট্রা’ গাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়ার খবর আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে হেডলাইন হয়েছিল। এক হিসাবে দেখা যায় দাঙ্গায় গুজরাটের দু’হাজার কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছিল। ওই সাম্প্রদায়িক হিংসা আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীদের ভীতিগ্রস্ত করে তোলে। শিল্পপতিদের ধারণা ছিল পরে গোলমাল আরও বাড়বে। সেই বছর সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে গুজরাতে ফরেন ডায়রেক্ট ইনভেস্টমেন্ট (এফডিআই) আসা একেবারে বন্ধ হয়ে যায়।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালদিলদার নগর - Aditi Dasgupta
২৭ মে ২০২৪ | ১৩৭ বার পঠিতঘরে এলে নাকি গেলে দেহলীটি ছুঁয়ে? নিশ্চিত না জানি। যেই পথে তুমি গেলে সাগরের ঢেউয়ে --- সেই পথে আমি তো উজানী !
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজামোবাইলে ‘না’ নির্বাচনে কমিশনের! - অর্ণব মণ্ডল
২৭ মে ২০২৪ | ৩৯৭ বার পঠিতসম্ভবত, কোনও ভোটার যাতে পোলিং বুথে ঢুকে ছবি তুলতে বা ভিডিও করতে না পারেন, সেই জন্যই মোবাইল ফোন, ক্যামেরা বা এই ধরনের কোনও রকম বৈদ্যুতিন যন্ত্র নিয়ে বুথে প্রবেশের ওপরে এই নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। কিন্তু, ভিডিও বা ছবি তো নির্বাচনী স্বচ্ছতার জন্য আরও বেশি করে প্রাসঙ্গিক। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্থানে সংবাদ মাধ্যমের ক্যামেরায় বুথের অভ্যন্তরের বিভিন্ন অনৈতিক কার্যকলাপের দৃশ্য ধরা পড়েছে। পোলিং অফিসারদের হুমকি দিয়ে সম্মিলিত ভাবে বুথ জ্যাম, দেদার ছাপ্পা – এসব ঘটনা তো আমাদের কাছে অতিপরিচিত। তাই বুথের ভেতরে যদি কেউ বা কয়েকজন মিলে গণ্ডগোল পাকানোর চেষ্টা করে, ভোটারদের কাছে ফোন থাকলে সেটার ছবি তোলা বা ভিডিও করা যাবে তৎক্ষণাৎ, যেটা পরে প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করে অপরাধীদের ধরার ক্ষেত্রে সেগুলো কাজে লাগতে পারে। শুধু ইভিএম মেশিনে একজনের ভোটদানের দৃশ্য যাতে অন্য কেউ না তুলতে পারে, সে বিষয়ে কড়া নজর রাখতে হবে।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালচালচিত্র এখন - সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায়
২৭ মে ২০২৪ | ৮৪৫ বার পঠিতচালচিত্র এখন সিনেমাটাও এই রীতি অনুসরণ করেই বানানো। যদিও অত পুরোনো না, এবং অত গভীর অনুসন্ধানেরও প্রয়োজন পড়তনা, কিন্তু সেটুকুও করার দরকার মনে হয়নি। এই সিনেমায় আশির দশকের কলকাতায় দিব্যি ল্যাজ তুলে ঘুরে বেড়ায় নীল-হলুদ বেসরকারি বাস, আশিতে সেসব বাস কেউ চোখে দেখেনি। শব্দ শোনা গেলে তারা হয়তো নিউটাউন-নিউটাউন বলেও হাঁক পাড়ত। দেখা যায়, সবুজ অটো। নায়কের বৌয়ের নাম মাঝেমধ্যেই মিতা থেকে বদলে গীতা হয়ে যায়। এবং মিতা ওরফে গীতা মিনার্ভা থেকে উত্তরপাড়া যেতে নিয়মিত শিয়ালদহ স্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধরেন। শিয়ালদা থেকে উত্তরপাড়া ট্রেনে চড়ে যাওয়া একেবারে অসম্ভব কিছু না, কিন্তু সে তো নৈহাটি-ব্যান্ডেল হয়েও যাওয়া যায়, সাধারণভাবে সুস্থ লোকে ওই দিক দিয়ে নিয়মিত যায় না আর কি।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালতিন দশকের প্রাচীন টি - সমরেশ মুখার্জী
২৭ মে ২০২৪ | ১৯০ বার পঠিতব্যক্তির জীবনে তিনটি দশক বড় কম সময় নয়। এই দীর্ঘ সময়ে ঘরে বাইরে তার নিজস্ব পরিসরে অনেক কিছু বদলায়। পুরানো গাড়ি বাতিল হয়, নতুন গৃহে প্রবেশ হয়, পুরানো সম্পর্কে শ্যাওলা ধরে, নতুন অহং পুষ্ট হয়, পুরানো স্মৃতি ধূসর হয়, নতুন মানে খুঁজতে হয়। এমন নানা পরিবর্তনের প্রভাবে কখনো জীবনের কিছু সরল সমীকরণ ক্রমশ বিবর্তিত হয় জটিল অসমীকরণে। এসবের মাঝে তিন দশক ধরে একটি সামান্য টি-শার্ট কিভাবে এহেন সার্ভিস দিয়ে যায় ভেবে অবাক লাগে
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালমানুষ ঠকানোর গল্প! - Muhammad Sadequzzaman Sharif
২৭ মে ২০২৪ | ১৯৭ বার পঠিতআমার খালার ফোনে ফোন আসল একটা। উনার বিকাশ ( বাংলাদেশের অন্যতম সেরা মোবাইল ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান) একাউন্টের পিন নাম্বারে সমস্যা হয়েছে, ঠিক করাতে হবে। খালার সাথে কথা বলে ওরা বুঝছে এই মহিলা এগুলা কম বুঝে। ওদের আত্মবিশ্বাস এতো যে তারা বলছে যে বুঝে তার কাছে নিয়ে যান। খালা আমার কাছে আসতেছিল পথে মধ্যে আরেক 'বিশেষ ভাবে অজ্ঞ' একজনের সাথে দেখা, তিনি তাদের সাথে কথা বলে যেমন যেমন করতে হয় তেমন তেমন করে কাজ সমাধা করেছেন। খালা এরপরে আসছে আমার কাছে। এসে বলল তোমার কাছেই আসতেছিলাম, বিকাশের পিন ঠিক করতে হব বলে, পথে অমুকের সাথে দেখা, ও ঠিক করে দিল! আমি শুনেই বুঝলাম এইটা গন কেস! বললাম, খালা বিকাশে টাকা কত ছিল? খালা বলল চার পাঁচ হাজারের মতো। আমি বললাম, ব্যালেন্স দেখেন, সম্ভবত এক টাকাও নাই! খালা বলে আরে না, ওরা তো পিন ঠিক করার জন্য বলছে। আমি বললাম, আপনে দেখেন! দেখা হল, ফিনিশ! এক টাকাও নাই!
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালদোলজ্যোৎস্নায় শুশুনিয়ায় - ১৩ - সমরেশ মুখার্জী
২৬ মে ২০২৪ | ১৮৫ বার পঠিতআশির দশকে যাদবপুরের কয়েকটি ছাত্রছাত্রী শুশুনিয়া পাহাড়ে গেছে শৈলারোহণ অভ্যাস করতে - সেই ভিত্তিতে এই আখ্যান … ঈশু বলে, "দ্যাখ জেঠু, এই ক্যাম্পিংয়ে একমাত্র গৌরব ছাড়া আমরা আর কে কতটা রক ক্লাইম্বিং করতে পারবো জানি না তবে আজকের এই আলোচনাটা খুব এনজয় করলাম। অনেক কিছু জানলাম। এর আগে কোনোদিন এমন স্পর্শকাতর বিষয়ে এভাবে খোলামেলা আলোচনা কারুর সাথে হয়নি। তাই এই আউটিংটা বহুদিন মনে থাকবে। থ্যাঙ্কস জেঠু। তোকে প্রায়শঃই চ্যাংড়ামি করতে দেখে ভাবতাম তুই একটা লঘুচিত্ত, চপলমতির ছেলে। তুই যে এমন সব সংবেদনশীল বিষয়েও এতো সাবলীল ভাবে আলোচনা করতে পারিস, জানা ছিলো না। এবার চল আমরা শুতে যাই, অনেক রাত হয়েছে। কাল সকালে তাড়াতাড়ি উঠতে হবে।" তখনও সুমন জানতো না, আগামীকাল গভীর রাতে ওকেই আবার এই কথাটা বলতে হবে ঈশুকে, অন্য পরিস্থিতিতে
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাকাদামাটির হাফলাইফ - ইট পাথরের জীবন - ইমানুল হক
২৫ মে ২০২৪ | ২৩৮ বার পঠিতযে বাড়িতে সত্যপীরের পালা, সে বাড়ির ছেলে মেয়েরা লোকেদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলে আসতো। সত্যপীরের ভূমিকায় যিনি অভিনয় করতেন তাঁর হাতে থাকতো একটা বিরাট সাদা চামর। সেটা মাথায় বুলিয়ে তিনি আশির্বাদ করতেন। হিন্দু মুসলমান সবাই সেই আশির্বাদ নিতেন। ১০-২০ পয়সা করে দিতেন মায়েরা সত্যপীরের পালায়। কিশোর ঘোষালদা লিখেছেন, ১৯৮০ র মাঝামাঝি সত্যপীর সত্যনারায়ণ হয়ে গেল। তা, সত্যপীরের পালায় হিন্দু মুসলমান একতার কথা থাকতো।
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাসীমানা - ৪৮ - শেখরনাথ মুখোপাধ্যায়
২৫ মে ২০২৪ | ১১৫ বার পঠিতস্যর স্ট্র্যাফোর্ড আর দ্বিতীয়বার দেখা করেননি গান্ধীর সঙ্গে, করে লাভ ছিল না। তিনি অবিশ্যি সত্যি-সত্যিই ভারতের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন, সেরকমই পরিকল্পনা ছিল তাঁর, কিন্তু সেই পরিকল্পনার ধার ধারতেন না তাঁর বস, উইনস্টন চার্চিল। সেই সময়কার ভাইসরয় লিনলিদগোও চার্চিলেরই দলে। ক্রিপ্সের মতো অনেক সোশ্যালিস্ট দেখা আছে তাঁদের। হামবাগ সব! জওহরলাল আর সেই সময়কার কংগ্রেসের রাষ্ট্রপতি মৌলানা আজাদ অবিশ্যি ক্রিপসের সঙ্গে একমতই ছিলেন, ছিলেন এমনকি রাজাগোপালাচারিও, যদিও লীগের ব্যাপারে কংগ্রেসের অবস্থানের প্রতিবাদে কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন রাজাগোপালাচারি নিজে। এখন গান্ধী একাই বিরোধীপক্ষ, যদিও নিজে গান্ধী মনে করেন না তা। তিনি মনে করেন সমস্ত দেশবাসী তাঁর পক্ষে। তিনি একবার সঙ্কেত দিলেই প্রায় প্রতিটি ভারতবাসী নেমে পড়বে রাস্তায়, তাদের মুখে থাকবে একটাই কথা, ভারত-ছাড়! যদি নিজে থেকে না ছাড়, আমরাই ছাড়াব তোমাদের। করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে!
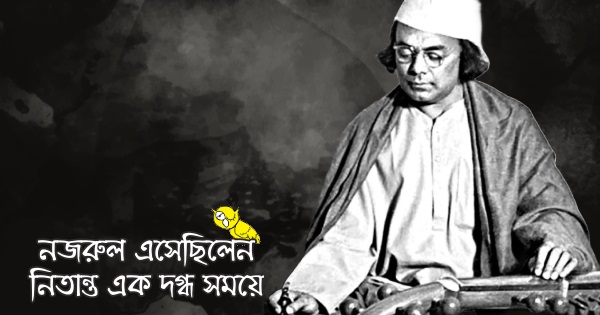 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজানজরুল এসেছিলেন নিতান্ত এক দগ্ধ সময়ে - সৈয়দ তৌশিফ আহমেদ
২৫ মে ২০২৪ | ৩৬৫ বার পঠিতপ্রতিকূলতার মুখে দাঁড়িয়ে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবনা যেভাবে প্রত্যাঘাত করেছে, সেটাকেই নজরুল শব্দের স্বচ্ছন্দ গতিতে রূপান্তর ঘটিয়ে গেছেন বরাবর, কিছুটা একবগগা এবং ছেলেমানুষের মতই। গূঢ় দর্শন তাঁর লেখার বাঁধনহারা উচ্ছলতায় খাদ মেশায় নি কখনও, তেমনই পুনরাবৃত্তিও পিছু ছাড়েনি। নজরুল ঠিক এখানেই স্বেচ্ছাচারী অসংযমী অসচেতন, এবং তাঁর সৃষ্টির অনেকাংশই গভীর ভাবলোকে অনুত্তীর্ণ। তবে ওই ঐচ্ছিক খামতিগুলোই কি তাঁকে অনন্য করেনি? তিনি তো একাই হয়ে উঠেছেন একটা ঘরানার আদি ও অন্ত। পূর্ব ও উত্তরসূরি না থাকা এক অদ্বিতীয় ধারা। এমনই এক তেজস্ক্রিয়তা, অর্ধ জীবনকালের সূত্র মেনে যার ফুরিয়ে যাওয়াটা নির্ধারিত। সেই ফুরিয়ে যাওয়াতেও অবশ্য তাঁর মস্ত সাফল্য।
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাবিপ্লবের আগুন - পর্ব ছয় - কিশোর ঘোষাল
২৫ মে ২০২৪ | ৩৩৬ বার পঠিতশুকনো পাতা দিয়ে বানানো গদিতে ভল্লা শুয়ে আছে। আজ পাঁচদিন হল সে একইভাবে শুয়ে আছে, নিশ্চেতন। তার মাথার কাছে বসে আছেন জুজাকের বউ। জুজাক দাঁড়িয়ে আছেন পায়ের দিকে। আর নিচু হয়ে বৃদ্ধ কবিরাজ হাতের নাড়ি পরখ করছেন ভল্লার। কিছুক্ষণ পর কবিরাজ ভল্লার হাতটা নামিয়ে দিলেন, বিছানায়। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, “জুজাক, আমার মন বলছে, ছোকরা এ যাত্রায় বেঁচে গেল। হতভাগার বাপ-মায়ের কপাল ভালো বলতে হবে।”
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজামহারাজ ছনেন্দ্রনাথের নামরহস্য - রমিত চট্টোপাধ্যায়
২৫ মে ২০২৪ | ৪৪১ বার পঠিতব্যস, এই সুযোগের অপেক্ষাতেই তো ছেনু ছিল, এক ছুটে দুধের গ্লাস হাতে তেতলার সিঁড়িতে উঠে পড়ল। এবার পা টিপে টিপে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে সিঁড়ি দিয়ে তেতলায় পৌঁছে ভালো করে তাকিয়ে দেখে নিলো কেউ আছে কিনা। যখন দেখতে পেল চারিদিক ফাঁকা, কেউ তার দিকে নজর রাখছে না, তখন গ্লাস থেকে এমন করে এক চুমুক দুধ খেলো, যাতে চলকে কিছুটা দুধ মুখ বেয়ে নেমে আসে, তারপর একটা বিচ্ছিরি মুখ করে কোনোক্রমে ঢোঁক গিলে সেই এক চুমুক দুধ গলা দিয়ে চালান করে নিচু হয়ে বসে ড্রেনের মুখটায় বাকি দুধটা আস্তে করে ঢালতে লাগল। ঢালতে ঢালতেও কড়া নজর চারদিকে, এই বুঝি কেউ দেখে ফেলল। ধীরে ধীরে পুরো দুধটাই ঢালা হয়ে গেলে আস্তে করে উঠে আবার সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এল।
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাস্লোভাকিয়া ৪ - হীরেন সিংহরায়
২৫ মে ২০২৪ | ২৩৮ বার পঠিতব্রাতিস্লাভায় সিটি ব্যাঙ্কের নবীন কর্মী মারেক পটোমা বলেছিল নিজের দেশ না হলে আইস হকিতে স্লোভাক প্লেয়ারদের জায়গা জুটবে না তাই আমরা আলাদা হয়েছি! দেশ ভাগের এর চেয়ে জোরালো যুক্তি আমি অন্তত খুঁজে পাই নি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে উইলসন ডকট্রিন মাফিক ইউরোপে স্বায়ত্ত শাসনের যে দাবি উঠেছিল তার ফলে পুরনো অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্যের অংশ বিশেষ মিলে তৈরি হলো চেকোস্লোভাকিয়া, এই মাত্তর ১৯১৮ সালে। ক্যাথলিক ধর্মের প্রাধান্য দুই অঞ্চলে, চেকের সঙ্গে স্লোভাক ভাষা প্রায় ৮৫% মেলে; আমার প্রাক্তন সহকর্মী ইভেতার (এখন আবু ধাবিতে) কাছে গল্প শুনেছি – অফিসে সে কিছু নিয়ে আলোচনা করছে এক চেক কলিগের সঙ্গে। আরেক স্থানীয় সহকর্মী জিজ্ঞেস করে, তোমরা কোন ভাষায় কথা বলছ? ইভেতা বলে, নিজের নিজের মতন, আমি স্লোভাক এবং উনি বলছেন চেক! আমাদের হিন্দি/উর্দু সংলাপের মতন।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালহাটুয়া সাধু ভোটুয়া ফকির - Naresh Jana
২৫ মে ২০২৪ | ৩৭৬ বার পঠিতসাধু হন্টন
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালভোটুৎসবে ভাট - এত বুড়ো কোনোকালে হব নাকো আমি - সমরেশ মুখার্জী
২৫ মে ২০২৪ | ১৬৩ বার পঠিত৪২% প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে ৬৩ শীত পার করেও আমার লেখ্যভঙ্গিতে লঘু রম্যরসময়তার প্রবণতা গেল না। অথচ ঐ রস উচ্চমার্গীয় আঙ্গিকে পেশ করার যোগ্যতাও নেই। তাই ওসব ধ্রুপদী পাঠকের ঋদ্ধরুচির উপযোগী নয়। ফলে তাঁদের রুচিশীল মন্তব্যে শালীন বিশেষণে অল্পাধিক উষ্মা, বিরক্তির প্রকাশ হয়ে পড়ে - যেমন “ঘাসবিচালি টাইপ রসিকতা”। তাতে অবশ্য আমি বিশেষ বিচলিত হই না। বিড়ম্বিতবোধও করি না। বরং তা নিয়েও আবার “খেলো টাইপস” রসিকতা করে ফেলি - এই যেমন এখন করছি।
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাশ্রী শ্রী উনিজি কথামৃত - সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায় ও কণিষ্ক
২৪ মে ২০২৪ | ৩০৮৬ বার পঠিতপ্রকাশিত হলো দুই মলাটে বৈদ্যুতিন উনিজি কথামৃত। লিখেছেন সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায়, এঁকেছেন নবীন শিল্পী কণিষ্ক। শিল্পীর সম্পর্কে বেশি জানা যায়নি, তিনি রাতের অন্ধকারে মেলবক্সে ছবির বান্ডিল ফেলে দিয়ে গেছেন। জানিয়েছেন উনিজির প্রতি অনুগত থাকতে চাইলে মাথা বর্জন করা ভালো, আর অনুগত থাকতে না চাইলে গর্দান যাওয়ার সম্ভাবনা, সুতরাং আগে থেকে মুন্ডু বিসর্জন দেওয়াই বিধেয়। নামিয়ে নিন, ছড়িয়ে দিন - উনিজি কথামৃত - পিডিএফ সংস্করণ।
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাভক্স পপুলি - যদুবাবু
২৪ মে ২০২৪ | ১২৪৯ বার পঠিতধরা যাক আমাদের n-সংখ্যক ভোটার আছে, n বিজোড় সংখ্যা (অর্থাৎ “টাই” অসম্ভব)। প্রত্যেক ভোটারের ঠিক বিকল্পে ভোট দেওয়ার সম্ভাবনা ধরা যাক pc, এবং সবার ভোট পড়ে গেলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে “মেজরিটি রুল” অনুযায়ী, অর্থাৎ যে সবথেকে বেশি ভোট পাবেন, সেটিই আমাদের গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত। কনডরসে-র উপপাদ্যে এও ধরে নেওয়া হয়, যে, প্রত্যেক ভোটার ‘স্বতন্ত্র’, ‘দক্ষ’ এবং ‘আন্তরিক’। ‘স্বতন্ত্র’ – অর্থাৎ যে যার নিজের ভোট দিচ্ছেন বা একজনের পছন্দ আরেকজনকে প্রভাবিত করে না। ‘দক্ষ’ – অর্থাৎ, প্রত্যেকের ঠিক বিকল্প খুঁজে নেওয়ার সম্ভাবনা অর্ধেকের থেকে বেশি, যত সামান্যই হোক, এক্কেবারে র্যান্ডম গ্যেস অর্থাৎ ইকির-মিকির-চামচিকির করে আন্দাজে যা-ইচ্ছে-তাই একটা বোতাম টিপে দেওয়ার থেকে তার প্রজ্ঞা বা দক্ষতা একচুল হলেও বেশি। আর শেষ অ্যাজ়াম্পশনের কথা আগেও লিখেছি, ভোটার-রা ‘আন্তরিক’, সিরিয়াস-ও বলা যায়—কেউ ইচ্ছে করে ভুলভাল ভোট দিয়ে নষ্ট করছেন না।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালদ্য নজরুল ফাইলস - সৈয়দ তৌশিফ আহমেদ
২৪ মে ২০২৪ | ২৮৩ বার পঠিত হরিদাস পাল
হরিদাস পালকিষেণজি মৃত্যু রহস্য - পর্ব ১০ - বিতনু চট্টোপাধ্যায়
২৪ মে ২০২৪ | ১৬৩ বার পঠিতঝুপ করে অন্ধকার নামল জঙ্গলমহলে। সাপধরা বুথ পেরিয়ে বাসু ভকতের গাড়ি এগোচ্ছে পিচ রাস্তা ধরে, জামবনির দিকে। জঙ্গলে আবছা অন্ধকারে বাসু ভকত কিংবা চালক গাড়ির দূর থেকে দেখতেও পেলেন না, গাছের গুঁড়ি ফেলে রাস্তা আটকে রেখেছে ঝাড়খন্ড পার্টির লোকজন। বিকেল থেকেই রাস্তার ধারে গাছের আড়ালে অপেক্ষা করছিল প্রচুর মহিলা-পুরষ এবং তীর, ধনুক নিয়ে সশস্ত্র ঝাড়খন্ডি বাহিনী। সরকারি গাড়ি গাছের গুঁড়ির সামনে থামলেই জঙ্গল থেকে বেরিয়ে ব্যালট বাক্স নিয়ে চম্পট দেবে তারা। কিন্তু পঞ্চায়েত ভোটের সন্ধ্যায় ব্যালট বাক্সের গাড়ি নয়, পাঁচামির জঙ্গলের ধারে ঝাড়খন্ডিদের তৈরি করা ব্যারিকেডের সামনে এসে থামল বাসুদেব ভকতের গাড়ি।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালসাম্রাজ্যবাদ: যুদ্ধই ইতিহাস, বর্তমান, ভবিষ্যৎ - Bhattacharjyo Debjit
২৪ মে ২০২৪ | ১৬৮ বার পঠিতবিশ্বায়নের সময় জুড়ে পিছিয়ে পড়া দেশগুলিতে লগ্নি পুঁজির ফাটকা প্রসারের হাত ধরে এবং সামন্তশ্রেনীর অংশের মিলিত বন্ধনে গড়ে উঠেছে নব্য আমলাতান্ত্রিক মুৎসুদ্দী পুঁজিপতিশ্রেনী। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, এদেশের আম্বানি-আদানি গোষ্ঠীদের। যাঁদের দ্বারাই আজ মূলত তৃতীয় বিশ্বে(এ দেশে) সাম্রাজ্যবাদীদের একচেটিয়া লগ্নি পুঁজির লুণ্ঠন অব্যাহত। তবে যেহেতু এই সময় সাম্রাজ্যবাদ স্বল্পমেয়াদি সময়ে একচেটিয়া ফাটকা মুনাফার উপরে বেশি ঝুঁকে পড়ে সেহেতু উৎপাদন - উৎপাদনশীলতা বিশ্বব্যাপী ব্যাপকভাবে কমতে থাকে যা পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কে মূলে ধাক্কা দেয়(যা নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করছেন বহু পুঁজিবাদী অর্থনীতিবিদেরা)। ফলে অতি-মুনাফার লোভ, বাজার দখলের প্রয়োজনে পুঁজির বর্ধিত পুনরুৎপাদনের স্বার্থে যুদ্ধ প্রায়শই প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তবে এ পর্বে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি সবসময়ই তৃতীয় বিশ্বের ঘাড়ের উপরে বন্দুক রেখে যুদ্ধ চালাতে চায় এবং নিজেরা সরাসরি সেই যুদ্ধে যুক্ত না হয়ে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অন্যান্য পিছিয়ে পড়া দেশের 'পুতুল' সরকারের মাধ্যমে যুদ্ধ পরিচালনা করতেই তদপর হয়ে উঠে।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালদিলদার নগর - Aditi Dasgupta
২৩ মে ২০২৪ | ২২১ বার পঠিতকপিশার কোল ঘেঁষে আমার মদিনা
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালতোমার বাস কোথা যে… - ৩ - Nirmalya Nag
২৩ মে ২০২৪ | ৩২৪ বার পঠিত“অঙ্কোলজিস্ট! কেন? ওনার কি… আমরা তো ভাবছিলাম টিবি হয়েছে,” বলল বিনীতা। “না ম্যাডাম। টিবির টেস্ট রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। আমার মনে হচ্ছে অঙ্কোলজি রিলেটেড কিছু হয়েছে স্যারের। ডক্টর বিশ্বাসের সাথে আমার ভাল আলাপ আছে। আমি ওনাকে বলে দেব। উনি রোজ বসেন, আপনারা কালই অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে নিন। আমি ওনার নম্বর আর হাসপাতালের নম্বর দুটোই দিয়ে দিচ্ছি,” বললেন শ্রীবাস্তব। “কাল হবে না,” এতক্ষণে মুখ খোলে অরুণাভ, “কাল অফিসে একটা খুব ইম্পরটান্ট মিটিং আছে।” “কিন্তু স্যার…” “বললাম তো কাল হবে না।” কথা শেষ করে দেওয়ার ভঙ্গিতে বলল অরুণাভ। স্বামীকে ভালই চেনে বিনীতা, তাই কালকের দিন নিয়ে আর কথা বাড়াল না সে। বলল, “আপনি নম্বরটা দিন। পরশুর জন্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট করব।”
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাগালুডি - নরেশ জানা
২৩ মে ২০২৪ | ৪৫৬ বার পঠিতগাঢ় অন্ধকারে ডুবে রয়েছে ভারতের আদিতম রেল স্টেশন। জরুরি কোনও বিদ্যুৎ সংযোগে ছোট্ট স্টেশনটার বাইরে একটা সোডিয়াম ভেপারের আলো পড়েছে টিকিট ঘরের বাইরে টালির চালে বসানো বোর্ডের ওপর। পলিমারের নীল বোর্ডের ওপর সাদা রঙে দেবনাগরী হরফে লেখা গালুডিহি! সেই আলোর এক চিলতে পড়েছে সামনের রেল লাইনের ওপর। অনায়াসে পায়ে হেঁটেই লাইন টপকে আমরা ঢুকে পড়লাম টিকিট ঘরের ভেতর। আমরা দাঁড়িয়ে আছি ১৩৩ বছর আগে তৈরি হওয়া একটি প্রাচীন রেল স্টেশনে! ১৮৮৭ সালে নাগপুর থেকে ছত্তিশগড় রেল লাইন পাততে শুরু করলো বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে কোম্পানী যা শেষ অবধি বিলাসপুর হয়ে আসানসোল অবধি এগিয়ে গেল। আর তার অব্যবহিত পরেই শুরু হল মুম্বাই থেকে কলকাতা অবধি রেললাইন পাতার কাজ ভায়া এলাহবাদ! ১৮৮৭ সাল ধরলে অবশ্য বছরটা ১৩৫ হওয়া উচিৎ কিন্তু আরও ২ বছর কমিয়ে বললাম এই কারনে যে প্ল্যাটফর্মের সেই আদি অকৃত্তিম ওজন মাপার যন্ত্রটা দেখলাম মরছে ধরা দেহ নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।
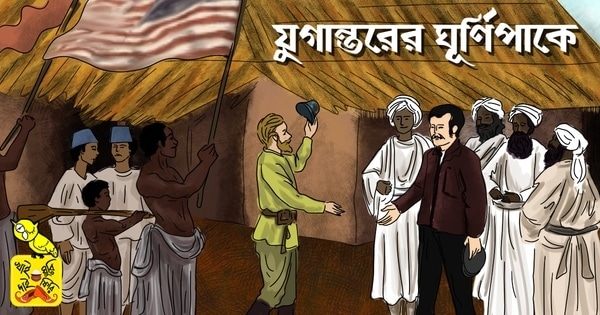 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাডেভিড লিভিংস্টোনের খোঁজে-১৪১ - হেনরি মর্টন স্ট্যানলে
২৩ মে ২০২৪ | ৭৩ বার পঠিত৩০ তারিখে আমরা খোঞ্জে পৌঁছলাম, মাটির থেকে অনেকটা উঁচুতে দৈত্যাকৃতির সিকামোর আর বাওবাব গাছের পাতার বিশাল চাঁদোয়ার কারণে জায়গাটা উল্লেখযোগ্য। খোঞ্জের সর্দার চারটে গ্রামের গর্বিত মালিক, তার থেকে সে পঞ্চাশ জন সশস্ত্র লোককে এক ডাকে হাজির করতে পারে; তবুও ন্য়ামওয়েজির বাসিন্দাদের প্ররোচনায় এই লোকটা আমাদের ঠেকানোর জন্য প্রস্তুত ছিল, কারণ আমি তাকে মাত্র তিন ডোটি অর্থাৎ বারো গজ কাপড় হঙ্গা হিসাবে পাঠিয়েছিলাম।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালদোলজ্যোৎস্নায় শুশুনিয়ায় - ১২ - সমরেশ মুখার্জী
২৩ মে ২০২৪ | ১১৮ বার পঠিতআশির দশকে যাদবপুরের কয়েকটি ছাত্রছাত্রী শুশুনিয়া পাহাড়ে গেছে শৈলারোহণ অভ্যাস করতে - সেই ভিত্তিতে এই আখ্যান … মনোবৈজ্ঞানিক ডঃ সুশীল মজুমদার, দীপদার বিশেষ পরিচিত। একদিন সুমনকে ওনার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে বললেন, সুশীলদা, এ হচ্ছে সুমন, যাদবপুরে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে। ওর মানব চরিত্র, কমপ্লেক্স এসব নিয়ে খুব কৌতূহল। আমায় নানা প্রশ্ন করে। আমি অনেককিছুর ঠিকঠাক জবাব দিতে পারি না। আপনি তো আজকাল বাড়িতেই থাকেন প্রায়। যদি মাঝেমধ্যে ওকে আসতে এ্যালাও করেন, ওর কিছু কৌতূহল নিরসন করেন, ওর ভালো লাগবে
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালমুসলমানদের বদলানো যাবেনা - Partha Banerjee
২৩ মে ২০২৪ | ৪১১ বার পঠিতআধুনিক যুগের আধুনিক মনোভাবের মুসলমানদের কারুর বাড়িতেই চারটি স্ত্রী নেই, এবং অসংখ্য বাচ্চা নেই। আগেকার দিনে হয়তো ছিল, ঠিক যেমন অন্ধকার যুগে হিন্দুদের কুলীন বামুনরা পঞ্চাশটা বিয়ে করতো, আর হিসেব-না-থাকা সন্তানের জন্ম দিয়ে কিশোরী বৌদের বিধবা করে দিয়ে মরতো। সাধারণ ঘরে মুসলমানদের যদি আট দশটা ছেলেমেয়ে হতো, সে তো হিন্দুদের ঘরেও হতো। আমার বাবারা ছিল ন-জন ভাইবোন। আমার মায়েরাও তাই। বিজেপি আরএসএস বিশ্ব হিন্দুদের মতো উগ্রপন্থীরা তো এসব প্রচার করবেই। কিন্তু লিবারাল বাঙালি হিন্দুরা কি তাদের মনোভাব বদলেছে?
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালদুষ্টু গরু - দৌরাত্ম্য ও প্রতিকার - সমরেশ মুখার্জী
২২ মে ২০২৪ | ৮৯৮ বার পঠিতগুরুচন্ডালিতে কিছু দুষ্টু গরুর দৌরাত্ম্য রোখার সম্ভাব্য উপায় প্রসঙ্গে এই প্রস্তাবনা। উদার গুরু তা করতে চাইবে কিনা বা চাইলেও তা করা সম্ভব কিনা জানি না
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালদিলদার নগর - Aditi Dasgupta
২১ মে ২০২৪ | ৩১৩ বার পঠিতদিলদার নগরের ঠিকানা গুছিয়ে না রাখলে জীবন কোথা?
- আরও বুলবুলভাজা ... আরও হরিদাস পাল ...
-
গুরুচণ্ডা৯-র গ্রাহক হোন
কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে গুরুচণ্ডা৯-র গ্রাহক হোন। গুরুচণ্ডা৯তে প্রকাশিত লেখাগুলি পেতে চাইলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যুক্ত হোন, অথবা, আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলটির গ্রাহক হোন।
- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই
- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... )
(লিখছেন... )
(লিখছেন... )
(লিখছেন... )
(লিখছেন... Shamik Roychowdhury, upal mukhopadhyay, যোষিতা)
- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন
(লিখছেন... )
(লিখছেন... অরিন, অরিন, সমরেশ মুখার্জী)
(লিখছেন... b, Amit, হীরেন সিংহরায়)
(লিখছেন... যোষিতা, Muhammad Sadequzzaman Sharif, যোষিতা)
(লিখছেন... হীরেন সিংহরায়, মোহাম্মদ কাজী মামুন )
- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... অরিন, অরিন, অমিতাভ চক্রবর্ত্তী)
(লিখছেন... সমরেশ মুখার্জী, ছোট মুখে , সমরেশ মুখার্জী)
(লিখছেন... দেখতে থাকুন, dc, এক্সিট পোল ভোট শেয়ার)
(লিখছেন... kk, দীপ, dc)
(লিখছেন... )
- কি, কেন, ইত্যাদি
- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...
- আমাদের কথা
- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...
- বুলবুলভাজা
- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...
- হরিদাস পালেরা
- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...
- টইপত্তর
- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...
- ভাটিয়া৯
- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...