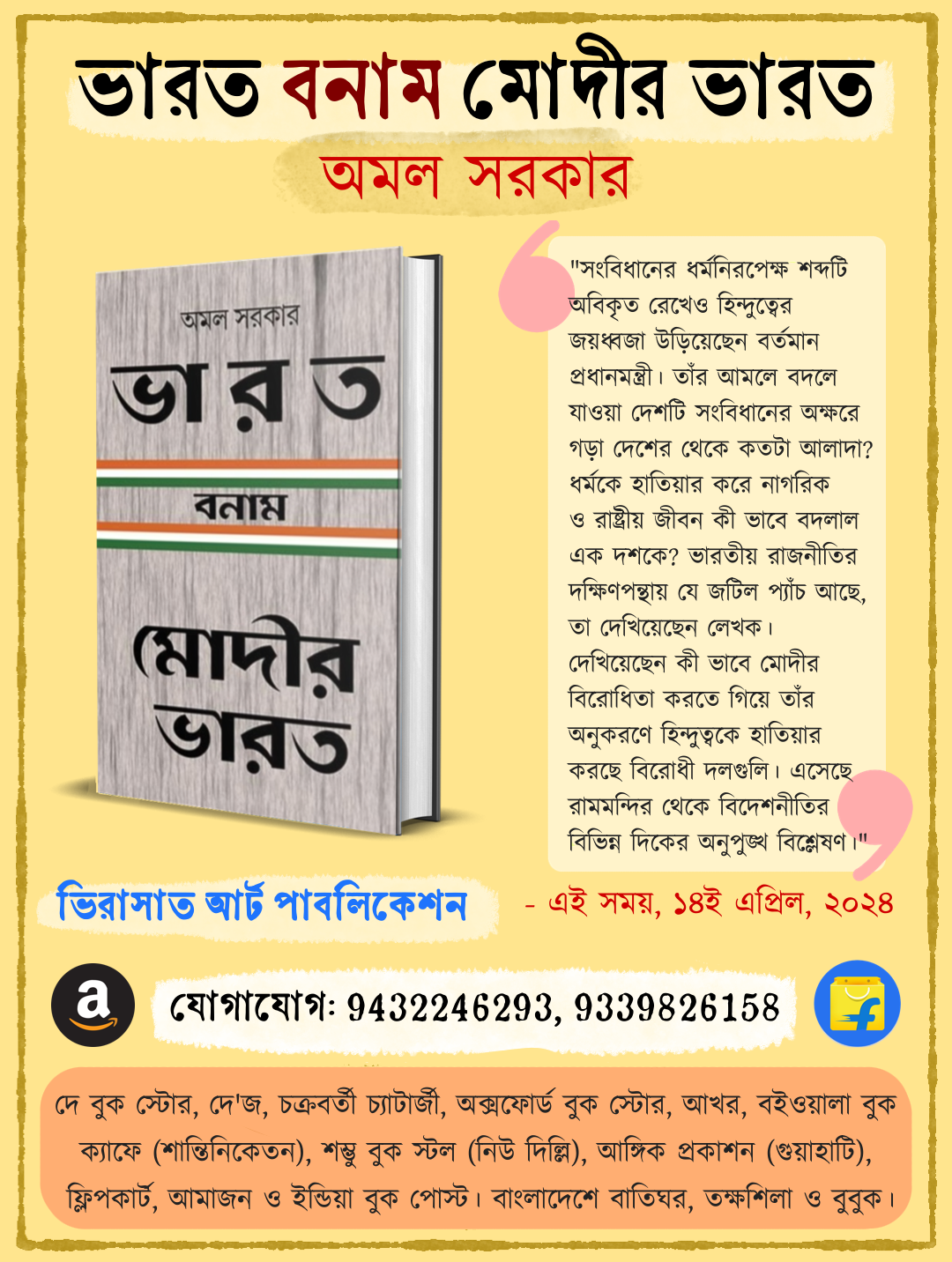- হরিদাস পাল ব্লগ

-
রাঙামা আর যবের ছাতু
Dipankar Dasgupta লেখকের গ্রাহক হোন
ব্লগ | ১২ জুলাই ২০২১ | ২৯২২ বার পঠিত | রেটিং ৪.৫ (২ জন) - "এ যব দোষের নয়, গুণের কেবল।
মেহ-পিত্ত-কফ হবে মধুর শীতল।।
নানা কর্ম্মে হিতকর নানা গুণনিধি।
নানারূপ রোগে হয় যবমন্ড বিধি।।
যব-ছাতু খেয়ে বাঁচে পশ্চিমের দীনে।
দেখহ যবের গুণ কেমন প্রধান।
যে তারে পেষণ করে রাখে তার প্রাণ।।
এখন তখন নাই বুঝে যদি খায়,
যবে বল যবে বল চিরকাল পায়।।"
তিনি ছিলেন আমার রাঙামা। আসলে রাঙা ঠাকুমা। বাবার মেজ কাকিমা। কিন্তু সকলের কাছেই তিনি একডাকে পরিচিত ছিলেন এই রাঙামা নামেই। একেবারে টুকটুকে গায়ের রঙের সঙ্গে আদরের ডাকের কী মিল! মাথায় কালো চুলের বড়ি খোঁপা। ছোটখাটো চেহারা। সংসারের হাজারো কাজ সামলে ওই বয়সেও মসৃন ত্বক। আদতে দ্বারভাঙার কন্যা। কবি যদিও বলেছেন, "যব-ছাতু খেয়ে বাঁচে পশ্চিমের দীনে," পশ্চিমে কিন্তু লোকপ্রিয় ছোলার ছাতু। উত্তরবঙ্গে বলতে শুনেছি, বুটের ছাতু। তা রাঙামা ছিলেন এই ছোলার ছাতু মাখার স্পেশালিস্ট। তাঁর হাতের তারে সেই ছাতু মাখা গোল বলের মতো দলার যে কী সুস্বাদ ছিল তা এখনও ভুলতে পারি না। সেই কাকভোরে বাগানে গিয়ে সাজি-ভরে জবা-টগর-অপরাজিতা-গুলঞ্চ-কল্কে ফুল তুলে আনতেন রাঙামা। সকালে চা-পর্ব শেষ হলে স্নান করে পুজো সেরে একটু বেলার দিকে কুটনো কোটার জন্যে সবজির ঝুড়ি নিয়ে বসতেন। আর সেই ফাঁকে অবরে সবরে আমরাও দাদুর বাড়িতে উপস্থিত থাকলে মা নরম গলায় বলতেন, "রাঙামা, আজ জলখাবারে ছাতু মাখা হবে নাকি?" ভারি অল্পে সন্তুষ্ট হওয়া মানুষ রাঙামা খুব স্নেহ করতেন সেজবৌমাকে। মা এলে নিরামিষ রান্না আর রাঙামাকে করতে দিতেন না। খুড় শাশুড়িকে নিজে হাতে রান্না করে খাওয়াতেন। ঠাকুরঘরের ঠিক উল্টোদিকে বিরাট উঠোন। বাঁদিকে ইঁদারার লাগোয়া বাগানে কালবৈশাখীর পর কয়েক পশলা বৃষ্টির জল পেয়ে শাক-সবজি ফনফনিয়ে বেড়েছে। ওদিকের জমিটা সতেজ নটেশাকে ভরে রয়েছে। পাশের মাচা থেকে ঝুলছে কচি ঝিঙে, ছোট ছোট উচ্ছে। মাচার নীচে টুকটুকে লাল টোম্যাটো আর সূর্যমুখী লঙ্কা। সবুজে-কালোয় মেশা সেই লঙ্কাগুলি বোঁটা থেকে মাটির দিকে না ঝুলে বর্শার ফলার মতো তাক করে রয়েছে আকাশের দিকে। মা বলেন, সিতুর দোকানের সরু, সুগন্ধি সাদা জুঁই ফুলের মতো তুলাইপাঞ্জি চালের গরম ভাতে এক চামচ সরের ঘি, নৈনিতাল আলুসেদ্ধ আর পাতলা মসুর ডালের সঙ্গে এই লঙ্কা থাকলে আর কিছুই লাগে না। ওদিকের বেগুন গাছগুলিতে অনেকগুলি সরেস বেগুন ঝুলছে। ইঁদারার চাতালের পাশে করবী গাছটাকে জড়িয়ে ডগা ছড়িয়েছে মিষ্টি কুমড়ো গাছ। ওপাশে হলুদ ফুলের মাঝে খয়েরি ছোপের শোভা ছড়িয়ে সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দিচ্ছে কচি কচি ঢ্যাঁড়শ। ঠাকুরঘরের জানালার গরাদের বাইরে কল পাড়ের দিকে যেতে আম গাছের ছায়া ছায়া মাটিতে রাঙামা কবে যেন ক'টা লাউয়ের বীচি পুঁতে দিয়েছিলেন। তা থেকে অংকুর গজিয়ে নিয়ম মাফিক বেড়ে উঠে বাঁশের বেড়া বেয়ে লকলক করছে লাউয়ের ডগা। মা আগেই ঠিক করে রেখেছিলেন, রাঙামাকে রান্না করে খাওয়াবেন নিরামিষ ঝোল-তরকারি। বাড়ির গাছের কুমড়ো এখনও কাঁচা। তবে সবজির ঝুড়িতে রয়েছে সবুজ পাড়ের উজ্জ্বল হলুদ রঙের মিষ্টি কুমড়োর ফালি। উল্টোদিকে ঝড়ুজেঠুর বাড়িতে আগের দিনই রান্নাঘরের চাল থেকে নামানো হয়েছে বিরাট বড় কুমড়ো। তার কিছুটা ইতানদি এসে দিয়ে গেছে। লাউডগা, বেগুন, ডুমো ডুমো কুমড়ো, ঝিঙে আর রাঙা আলু দিয়ে কাঁচালঙ্কা-কালোজিরে ফোড়নে মায়ের এই রান্না গরমের দিনে খেয়ে সকলের বড় আরাম। আর করবেন গ্যারানি। রাঙামার খুব প্রিয়। ভেজানো মটর ডাল ফেটিয়ে বড়া ভেজে রাঁধুনি, তেজপাতা, শুকনো লঙ্কা ফোড়নে পাতলা ঝোলে অনেকটা পোস্তবাটা, ঘি আর আদাবাটা।
অন্য সময় তো পাকের ঘরের রান্না সেরে বেলা দুপুরে আবার স্নান করে নিজের রান্না রাঙামাকেই ফুটিয়ে নিতে হত। রাঙাদাদু তো কত আগেই চলে গেছেন। ভালোপিসি পঁচিশ কিমি দূরে গার্লস স্কুলের জনপ্রিয় দিদিমনি। ছোটপিসি সারাদিন গোয়ালে গরুর পরিচর্যা আর বাগান নিয়ে ব্যস্ত। বাড়ির গরু আর পোষা কুকুরগুলির প্রতি ছোটপিসির বড় মায়া। মাটির বড় চারিতে জাবনা কেটে গুছিয়ে দেওয়া, গোয়াল পরিষ্কার করা এসবের জন্যে যাদবদা তো আছেই। তবু নিজে সব কিছু না দেখলে, গরুর গলায় হাত বুলিয়ে আদর করতে করতে না খাওয়ালে ছোটপিসির শান্তি হত না। বাবার কাকামণি ভালোদাদু তো দুঁদে উকিল। রেগে গেলে ফর্সা মুখখানা লাল। কিন্তু আমার সঙ্গে অন্য সম্পর্ক। মরসুমের প্রথম ফল, সবজি, মক্কেলের পুকুর থেকে তোলা জ্যান্ত রুই-কাতলা এলে নাতির জন্যে প্রথম বরাদ্দ। ভালোমাকে আমি দেখিনি। তিনি তো বড় আর সেজপিসিকে একদম ছোট রেখেই চলে গেছেন। ঠাকুরপোর যত্ন-আত্তি সব রাঙামার কাঁধে। বড় আর সেজপিসি বিয়ের পরে স্থানান্তরে। ভালোদাদুকে কোর্টে রওনা করে দিয়ে মায়ের আব্দার মতো একটা বড় কাঁসার বগিথালা নিয়ে বসতেন রাঙামা। তাতে চুড়ো করে নিতেন ছোলার ছাতু, উঠোনের রোদে দেওয়া কাচের বয়াম থেকে চামচে করে তোলা আম-তেল, উনানে সেঁকে নেওয়া শুকনো লঙ্কা, বাগানের গাছ থেকে ছোটপিসির ছিঁড়ে আনা লেবুর রস আর একটু লবন। বেশ অনেকক্ষণ ধরে মসৃন করে মাখার পর ছোট একটা দলা নিজের জন্যে আলাদা করে রেখে বাকিটা মাকে দিয়ে বলতেন ওতে একটু কাঁচা পেঁয়াজের কুচি তোমরা দিয়ে আর একটু মেখে নিয়ে সকলে মিলে খাও। সে স্বাদের ভাগ পেয়ে সেই ছোটবেলা থেকেই একটু একটু করে গড়ে উঠেছে আমার স্বাদ-সংস্কৃতি আর তার সঙ্গে রাশি রাশি মধুর স্মৃতি।


ছোলার ছাতুর কথা উঠল বটে কিন্তু আমাদের পরিবারে চৈত্র সংক্রান্তিতে বছর শেষের এক স্মরণীয় প্রথা ছিল 'ভাই ছাতু।' গ্রামবাংলার সাবেকি রীতি ছিল, পরিবারের মহিলারা বাড়ির কাছের কোন নদী বা জলাশয়ের ধারে দাঁড়িয়ে কুলোর বাতাস দিয়ে ছাতুর ধুলো উড়িয়ে একসঙ্গে বলে ওঠেন, "শত্রুর মুখে দিয়া ছাই, ছাতু উড়াইয়া ঘরে যাই।" সেই উড়তে থাকা ছাতুর ঝড় আর মেঠো পথের ধুলো ঢেকে দেয় পুরাতন বছরের শেষ সূর্যকে। নববর্ষ তো বটেই, ছোটবেলায় আমার কাছে চৈত্র সংক্রান্তির দিনটির আকর্ষণও তাই কম ছিল না। ওই দুটি দিন প্রতি বছর বাবা আমাদের নিয়ে যেতেন দাদুর ওখানে। সকালে স্নান করে বারান্দায় দাদু, বাবা আর আমি আসনে বসতাম। ভালো আর ছোটপিসিও স্নান করে প্রদীপ জ্বালিয়ে সামনে রাখতেন। পেতলের রেকাবিতে থাকত ধান-দূর্বা। আর ছোট একটা বেতের ধামায় নতুন ভাঙানো যবের ছাতু। সেই ছাতুর আবার গল্প আছে। ভালোদাদুর বাড়িতে মাসে একবার করে আসতেন এক বিধবা বোষ্টমী। গলায় কন্ঠী আর ঝোলানো সাদা কাপড়ের থলিতে জপের মালা। তিনি ছিলেন বোবা। হাতের তালি, ইশারা আর ঠোঁটের নড়া দেখে পিসিদের আর রাঙামার কথা ঠিক বুঝতেন। তাঁর কাছ থেকেই নেওয়া হত জাঁতায় ভাঙানো যবের ছাতু। ভাজা সোনামুগ আর মাসকলাইয়ের ডাল, দু-তিন রকমের বড়ি আর আমসত্ত্বও নিয়ে আসতেন বেতের ঝুড়িতে। বাড়ির কে কোনটা ভালোবাসে সব ছিল তাঁর জানা। কথা বলতে না পারলে কী হবে তাঁর জিনিসের তারিফ করলে খুশিতে তাঁর চোখদুটো হাসত। ছোটবেলায় দেখা বলিরেখা আঁকা সেই প্রশান্ত মুখখানি আজও যেন একদম স্পষ্ট দেখতে পাই। পিসিদের পাশে থাকতেন রাঙামাও। প্রথমে দাদু বাঁ হাত মুঠি করে সামনে প্রসারিত করে দিতেন। সেই মুঠির ওপরে রাঙামা পরপর তিনবার একটু একটু করে ছাতু দিতেন আর দাদু সেটা ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিতেন। রাঙামা 'ভাই ফোঁটা' না দিলেও প্রিয় ঠাকুরপোকে ছাতু দিতেন। বোনের দেওয়া ছাতু ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিলে সম্বৎসর ভাইয়ের যাবতীয় বিঘ্ন-বিপদ কেটে যায় বলেই প্রচলিত সংস্কার। আর তাই এই মাঙ্গলিক রীতি। এরপর পিসিরা বাবাকে ছাতু দিতেন একই ভাবে। আর তারপর দাদু আর বাবার দেখাদেখি আমিও জোরসে ফুঁ দিতাম রাঙামার দেওয়া ছাতুতে। পিসিরা হেসে বলত "বাবুলের ফুঁয়ের কত জোর! ও-ই তো ছাতু কত দূরে উড়িয়ে দিল, আর দেখাই গেল না।" ছাতু ফুঁ দিয়ে ওড়ানোর পর প্রণাম করলে ধান-দূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ। ভাই ফোঁটার মতো ভাই ছাতুর দিনটিতেও রাঙামা আমাকে একটা খাতা আর একটা পেনসিল দিতেন। ছাতু ওড়ানোর পর প্রত্যেকে আলাদা বাটিতে যবের ছাতু, ঘরে পাতা টক দই, সুমিষ্ট মালভোগ কলা আর নতুন আখের গুড় বা চিনি আর একটু জল দিয়ে পাতলা করে মেখে খাওয়া হত সেদিন সকালের জলখাবার। গ্রীষ্মের মরসুমে শরীর শীতল রাখতে আর পেট ঠান্ডা রাখতে এভাবেই শুরু হত ছাতু খাওয়া। মা অবশ্য অনেক সময় দইয়ের বদলে ছাতু-দুধ দিতেন। খুব গরম পড়লে ছাতুর সঙ্গে একটু পাকা তেঁতুল, নুন-চিনি আর মাটির কুঁজো থেকে ঠান্ডা জল গড়িয়ে পাতলা করে একবাটি দিতেন। আহা! প্রাণ জুড়িয়ে যেত। এই ছাতু-পর্বের পরে চৈত্র সংক্রান্তিতে বিকেলের জন্যে অধীর উত্তেজনা নিয়ে অপেক্ষা করতাম। কারণ, দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর রোদ পড়লেই একটা রিক্সা ডেকে ভালোদাদু আমাকে নিয়ে ওই কুলিক নদীর ধারে সুভাষগঞ্জে চড়কের মেলায় নিয়ে যাবেন। সেখানে আবার বহু বছর ধরে প্রতিবার সুঠাম চেহারার যাদবদা পিঠ ফুঁড়িয়ে বোঁ-বোঁ করে ঘোরে। ফেরার সময় মেলা থেকে দাদু আমাকে চরকি আর টমটমি কিনে দিতেন। বাড়িতে নিয়ে আসতেন চ্যাঙাড়ি ভর্তি মুচমুচে জিলিপি আর পাঁপড়। আমার জন্যে বরাদ্দ থাকত আরও কিছু কদমা আর রং-বেরংয়ের মন্দির, ঘোড়া, হরিণ আকৃতির চিনির রসের মঠ।
ছোটবেলার সেই সব স্মৃতি সব ফিকে হয়ে যাচ্ছে। তবে এখনও এই কলকাতা শহরে ফি বছর গ্রীষ্মের সময় বিশেষ দোকান থেকে সংগ্রহ করে নিয়ে আসি যবের ছাতু। আর আনি তাল পাটালি -- যার সঙ্গে আমার পরিচয় বড়জেঠুর সৌজন্যে। একবার কলকাতায় এলে জেঠু বললেন, "গোপীন, তোমাকে আজ একটা নতুন জিনিস খাওয়াব অফিস থেকে ফিরে।" জেঠু আমার নাম দিয়েছিলেন গোপীনাথ। তার থেকে গোপীন। চিরকাল ধবধবে সাদা ফিনফিনে ধুতি আর হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের স্টাইলে লম্বা-ঝুল শার্ট পরা জেঠু কাজ করতেন কয়লাঘাটার রেলের সদর দপ্তরে। আর সেখানকার কর্মচারি সমবায় সমিতির অন্যতম পরিচালক ছিলেন। সেই ক্যান্টিনে সুলভ মূল্যে সংসারের অনেক জিনিস পাওয়া যেত। আর পাওয়া যেত বিভিন্ন ধরণের ভাঙা বিস্কুটের মিশ্রিত সমাহার। সে এক চমৎকার জিনিস। নোনতা, মিষ্টি, ক্রিম আর এক রকম সার্কাস বিস্কুট। জেঠু নিয়ে আসতেন খুব কম দামে। তার প্রতি ছিল আমার বিশেষ আকর্ষণ। ভেবেছিলাম তেমন ধরণের কিছু হবে। সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে জেঠু ব্যাগ থেকে একটা বড় ঠোঙা বের করে আমাকে দিয়ে বললেন, "দেখ তো কী আছে? খেয়ে দেখ কেমন লাগে।" আমি প্রবল আগ্রহ নিয়ে দেখি ঠোঙার মধ্যে দেখতে ঠিক সন্দেশের মতো ঘিয়ে রঙের বড় বড় খন্ড। একটু ভেঙে যেই মুখে ফেলেছি কী অপূর্ব স্বাদ আর গন্ধ। জিভের মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছে রসের ধারা। জেঠু বললেন, শীতকালে খেজুর রসের নলেন গুড় আর পাটালি তো খেয়েছ। এটা হল গ্রীষ্মের পাটালি। তালের রস থেকে। গরম আটার রুটি, বাটি-ভর্তি মুড়ি বা ছাতু-দুধ আর চিঁড়ে-দুধ-কলার সঙ্গে মেখে খেয়েই দেখ একবার! সে জিনিস আমার এমন পছন্দ হল যে কলকাতা থেকে ফেরার সময় প্রতিবার জেঠু আমার জন্যে এই তালপাটালি আর আমার আর একটি প্রিয় জিনিস এক শিশি গুড়ের বাতাসা দিয়ে দিতে কখনও ভুলতেন না। এক সময় পশ্চিমবঙ্গ তালগুড় মহাসঙ্ঘ নামে এক সমবায় সংস্থার গুমটি ছিল শহরের বিভিন্ন প্রান্তে। আর ছিল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সামনে রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে থাকা ফ্যাকাশে নীল রঙের এক মোবাইল ভ্যান। সেই সব জায়গায় খাঁটি তালপাটালি, তালমিছরি তো পাওয়া যেতই। আর পাওয়া যেত আশ্চর্য প্রাকৃতিক পানীয় 'নীরা' -- সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কল্পলোকের সেই রহস্যময়ী নারীর মতোই যা ছিল সকলের কাছে পরম রমণীয়।
আজকের আধুনিক প্রজন্ম এমন সব আটপৌরে জলখাবারের মর্মই হয়ত বোঝে না। তবে আজও এই সব সাধারণ ঘরোয়া খাবার নিয়ে বসলে চোখের সামনে ভেসে ওঠে পৃথিবী থেকে একে একে চলে যাওয়া প্রিয় মুখগুলি যাঁদের স্নেহ, আর ভালোবাসা আমাদের শৈশব-কৈশোরের স্মৃতিকে এমন উজ্জ্বল করে রেখেছে।
পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কিত নীতিঃ এই লেখাটি ছাপা, ডিজিটাল, দৃশ্য, শ্রাব্য, বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিলিপিকরণ বা অন্যত্র প্রকাশের জন্য গুরুচণ্ডা৯র অনুমতি বাধ্যতামূলক। লেখক চাইলে অন্যত্র প্রকাশ করতে পারেন, সেক্ষেত্রে গুরুচণ্ডা৯র উল্লেখ প্রত্যাশিত। - আরও পড়ুনএকদিন শিখরভূমে -- উন্নয়নের জোয়ারে বিপর্যয়ের নীরব সাক্ষী তেলকুপি বা পঞ্চকোট - Dipankar Dasguptaআরও পড়ুনসেদিন সেতার বাজিয়েছিলেন পন্ডিত রবিশঙ্কর, ভাইয়ের কথা বলেছিলেন রালিয়াত বেন - Dipankar Dasguptaআরও পড়ুনট্রফি - ইন্দ্রাণীআরও পড়ুনমাথার পোকা -১ - Kishore Ghosalআরও পড়ুনবৈঠকি আড্ডায় ১৩ - হীরেন সিংহরায়আরও পড়ুনবৈঠকি আড্ডায় ১২ - হীরেন সিংহরায়আরও পড়ুনবৈঠকি আড্ডায় ১১ - হীরেন সিংহরায়
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
-
দ | ১২ জুলাই ২০২১ ২৩:২৭495746
বাহ বেশ লাগল। ছাতু নিয়ে আমারও বেশ কিছু স্মৃতি আছে। চৈত্র সংক্রান্তির দিন আমাদের বাড়িতে ছাতুমাখা খাবার প্রথা ছিল। ভাই ছাতু অবশ্য ছিল না। এর কথা রাণী চন্দের লেখায় পড়েছিলাম মনে হয়। বাংলার বাইরে ছাতু বেশ জনপ্রিয়। দিল্লি ছিলাম সময় গরমকালে রোজ ছাতুর শরবত বানিয়ে খেতাম। ছাতুর কচুরিও ভাল জলখাবার। তালপাটালিও খেয়েছি এই তো কয়েক বছর আগেও।
-
অমিতাভ চক্রবর্ত্তী | ১৩ জুলাই ২০২১ ০৮:০৮495751
ভালো লাগল। আর, চৈত্র সংক্রান্তিতে ছাতু ওড়ানোর অভিজ্ঞতার আরো অংশীদার পাওয়া গেল।
-
 Anindita Roy Saha | ১৩ জুলাই ২০২১ ১০:৫৪495753
Anindita Roy Saha | ১৩ জুলাই ২০২১ ১০:৫৪495753 বিহারী কায়দায় শক্ত করে মাখা ছাতুর একটি নোনতা দলা, সংগে কুট করে একটা কামড় কাঁচা লংকায়। লোলুপ চোখে দেখে ‘পিকু’ বলবে , “তোমার ঝাল লাগে না?”
-
Ranjan Roy | ১৩ জুলাই ২০২১ ১৮:৪৬495757
"সুগন্ধি সাদা জুঁই ফুলের মতো তুলাইপাঞ্জি চালের গরম ভাতে এক চামচ সরের ঘি, নৈনিতাল আলুসেদ্ধ আর পাতলা মসুর ডালের সঙ্গে এই লঙ্কা থাকলে আর কিছুই লাগে না।
--আমি আজও তাই ভাবি। আর ছোলার চেয়ে যবের ছাতু আমার পছন্দ। তাল পাটালি? সেতো অমৃত। বহুদিন খাইনি।
-
বিপ্লব রহমান | ১৭ জুলাই ২০২১ ০৫:৫৮495850
অপূর্ব উজ্জ্বল শৈশব স্মৃতি! খুব মায়াময় লেখনি।
লেখায় ছবিগুলো বাহুল্য মনে হয়েছে। সম্ভব হলে আগামীতে ফনটা বদলে নেবেন? খুব দৃষ্টি বান্ধব নয়
 গৌতম | 2405:201:801a:9845:9cae:67eb:15fc:4f | ১৫ এপ্রিল ২০২২ ২০:৩৪506440
গৌতম | 2405:201:801a:9845:9cae:67eb:15fc:4f | ১৫ এপ্রিল ২০২২ ২০:৩৪506440- তাল পাটালির কথায় শৈশবের স্মৃতি ভেসে এল।দাদু ছিলেন বঙ্গবাসি কলেজে , প্রতি গ্রীস্মে বৈঠকখানা বাজার থেকে নতুন তাল পাটালি নিয়ে আসতেন। সে এক অপূর্ব স্বাদ ! একবাটি মুড়ির উপর একটা বড় তাল পাটালির টুকরো পেলে যেন অমৃত পাওয়া হোত।এখন তো এইসব গল্পকথা !
-
Sara Man | ১৬ এপ্রিল ২০২২ ০৮:১৯506455
- তার মানে আমি ছাড়া নীরাপ্রাস ভালোবাসে এমন আর একজন আছে। নীরাপ্রাস সেই ভ্যানে আজও পাওয়া যায়। ঐ অপূর্ব স্বাদের কোনদিন প্রচার হলনা, এটাই দুঃখের।
 মহুয়া দত্ত | 106.212.0.247 | ০৬ এপ্রিল ২০২৩ ১৫:৫০518334
মহুয়া দত্ত | 106.212.0.247 | ০৬ এপ্রিল ২০২৩ ১৫:৫০518334- খুব ভালো লাগল
 &/ | 151.141.84.152 | ০৭ এপ্রিল ২০২৩ ০৪:০৭518376
&/ | 151.141.84.152 | ০৭ এপ্রিল ২০২৩ ০৪:০৭518376- ঈশ, কী যে ভালো লাগল! দারুণ!
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
-
গুরুচণ্ডা৯-র গ্রাহক হোন
কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে গুরুচণ্ডা৯-র গ্রাহক হোন। গুরুচণ্ডা৯তে প্রকাশিত লেখাগুলি পেতে চাইলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যুক্ত হোন, অথবা, আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলটির গ্রাহক হোন।
- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই
- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... )
(লিখছেন... অরিন)
(লিখছেন... kk, রমিত চট্টোপাধ্যায়, বিপ্লব রহমান)
(লিখছেন... Aranya )
(লিখছেন... পাপাঙ্গুল)
- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন
(লিখছেন... সৃষ্টিছাড়া, সমরেশ মুখার্জী)
(লিখছেন... Prabhas Sen, Ranjan Roy, পড়ুন)
(লিখছেন... সমরেশ মুখার্জী, Kishore Ghosal, সমরেশ মুখার্জী)
(লিখছেন... Muhammad Sadequzzaman Sharif, Muhammad Sadequzzaman Sharif, দীপ)
(লিখছেন... dc, পলিটিশিয়ান, dc)
- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... পাপাঙ্গুল)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... jsl)
(লিখছেন... অরিন, &/, অরিন)
(লিখছেন... lcm, পাঠক, সুকি)
- কি, কেন, ইত্যাদি
- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...
- আমাদের কথা
- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...
- বুলবুলভাজা
- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...
- হরিদাস পালেরা
- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...
- টইপত্তর
- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...
- ভাটিয়া৯
- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...
- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।