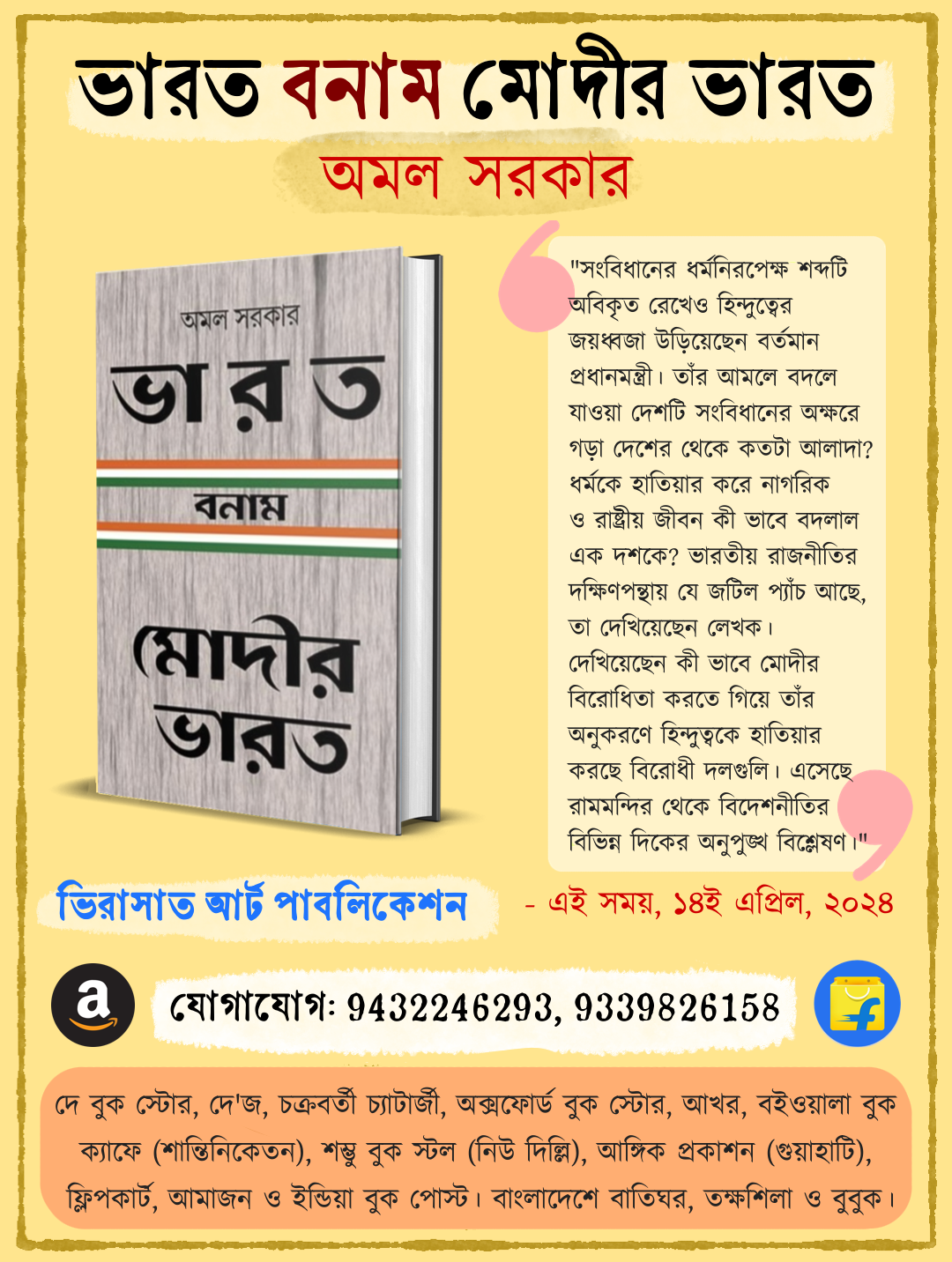- হরিদাস পাল আলোচনা বিবিধ

-
গল্পের শেষ, শেষের কবিতা
Nirmalya Nag লেখকের গ্রাহক হোন
আলোচনা | বিবিধ | ০৮ নভেম্বর ২০২০ | ২৮৪৫ বার পঠিত - দুই পাতার মধ্যে আঙুলটাকে পেজমার্কের মত রেখে বইটা বন্ধ করে জানলা দিয়ে বাইরে আপনি বাইরে তাকালেন। আপনি আছেন বাসে, বাইরে রাস্তা, গাড়ি যাচ্ছে, রিকশা অটো চলছে, হয়তো বৃষ্টি পড়ছে টিপটিপ করে, তার মধ্যে দিয়েই হেঁটে চলেছে মানুষজন, ছাতা নিয়ে বা না নিয়ে। আর ফুটপাথবাসীরা তাঁদের নিত্যদিনের কাজে ব্যাস্ত। বৃষ্টির সোঁদা গন্ধ ছাপিয়ে আপনি পেলেন কাঠের জ্বালে ভাত রান্নার গন্ধ। আপনার মনে হল কোনও শিল্পী হয়তো এই জীবনযাপনের একটা অসামান্য মুহূর্তকে ধরে ফেলতে পারতেন তাঁর ক্যানভাসে, বা ক্যামেরায়, বা কলমে। আর আপনি তা দেখে বা পড়ে মুগ্ধ হতেন, ছবি দেখে হয়তো বলতেন "কবিতার মত", আর কবিতা পড়ে ভাবতেন "এ তো জাগতিক হয়েও অপার্থিব"। ধরাছোঁয়ার মধ্যে থেকেও যেন কোথাও এগুলো আপনাকে টেনে নিয়ে যাবে এমন কোথাও যে জায়গার কথা আপনি জানতেনই না। কেন মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে আপনার এ সব কথা? আপনি শেষ করেছেন একটি গল্প, লম্বা শ্বাস ফেলেছেন, তারপর তাকিয়েছেন বাইরের দিকে কারণ আপনার অন্তর জুড়ে বসে অবস্থান করছে ওই গল্পের শেষ অক্ষরগুলো যাকে কবিতা বললে অত্যুক্তি হবে না।
তেমনই পাঁচটা কবিতার মত সমাপ্তি তুলে ধরা হল এখানে। চেনা গল্প, চেনা শেষ। তবু এই প্রিয় পঞ্চপল্লবকে ফিরে দেখার ইচ্ছে হল শেষ থেকে।
মহেশ -- শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
"অন্ধকার গভীর নিশীথে সে মেয়ের হাত ধরিয়া বাহির হইল। এ গ্রামে আত্মীয় কেহ তাহার ছিল না, কাহাকেও বলিবার কিছু নাই। আঙ্গিনা পার হইয়া পথের ধারে সেই বাবলাতলায় আসিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া সহসা হু হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। নক্ষত্রখচিত কালো আকাশে মুখ তুলিয়া বলিল, আল্লা! আমাকে যত খুশি সাজা দিয়ো, কিন্তু মহেশ আমার তেষ্টা নিয়ে মরেচে। তার চ'রে খাবার এতটুকু জমি কেউ রাখেনি। যে তোমার দেওয়া মাঠের ঘাস, তোমার দেওয়া তেষ্টার জল তাকে খেতে দেয়নি, তার কসুর তুমি যেন কখনো মাপ কোরোনা।"
বেঁচে থাকতে মানুষের যা যা প্রয়োজন তার মধ্যে প্রধান হল খাদ্য, বস্ত্র আর বাসস্থান। মনুষ্যেতর জীবদের বস্ত্রের দরকার পরে না, বাসস্থান বলতে কিছু একটা হয়তো থাকে, গৃহপালিত জীবদের সে ভাবনাটুকুও থাকে না। তাদের এক ও একমাত্র প্রয়োজন হল খাদ্য, যার মধ্যে অবশ্যই পরে সেই জিনিসটি যার অন্য নামই হল 'জীবন'। প্রখর গ্রীষ্মে, প্রবল অভাবে আর কিছুটা ধর্মের কারণে গফুরের জীর্ণ বাড়িতে জল আর খাবার বাড়ন্ত। দশ বছরের মেয়ের অতি কষ্টে জোগাড় করা খাবার জল যখন একান্ত প্রিয় ষাঁড়টি খেয়ে নিচ্ছিল, গফুরের আর মাথার ঠিক থাকল না। খুলে রাখা লাঙলের ফালের এক ঘায়েই মহেশের ভবলীলা সাঙ্গ হল। রাতের নিকষ কালো অন্ধকারে তারার আলোয় নতুন জীবনের সন্ধানে সকন্যা পথে নামে গফুর, যে জীবনকে এত কাল ঘৃণাই করে এসেছে সে। জমির কৃষক থেকে কারখানার শ্রমিক হয়ে ওঠার পিছনে এমন কত ঘটনা থাকে, তার হিসেব কেই বা কবে রেখেছে। সেকালেও কেউ রাখেনি, আজও কেউ রাখে না। কিন্তু গফুর কি কেবল মহেশের কথাই বলে গল্পের শেষে? ওই হাহাকারের মধ্যে আমরা যেন দেখি এক হয়ে গেল গফুর জোলা আর তার অতি প্রিয় অথচ তারই হাতে নিহত পশুটির জীবনযন্ত্রণা। খিদের সময়ে খাবার আর তেষ্টার সময়ে জল পায়নি দুজনের কেউই। গফুরের মত মানুষরা পায় না, তাদের ধর্ম বা জাত যাই হোক না কেন। তারা কেবল এক অজানা-অচেনা-অদেখা সৃষ্টিকর্তার আদালতে করুণ নালিশ রেখে যায় - ক্ষমা ক'রো না প্রভু। সেইটুকুই তাদের সম্বল, সেইটুকুই তাদের সান্ত্বনা।
জতুগৃহ - সুবোধ ঘোষ
"ওয়েটিংরুমের টেবিলের ওপর একটি ট্রে, তার ওপর পাশাপাশি দুটি শূন্য চায়ের পেয়ালা। কোথা থেকে কারা দু'জন এসে, আর পাশাপাশি বসে তাদের তৃষ্ণা মিটিয়ে চলে গেছে। রাজপুর জংশন আবার ঘুমিয়ে পড়ার আগে বয় এসে তুলে নিয়ে যাবে, ধুয়ে মুছে সাজিয়ে রেখে দেবে, একটা পেয়ালা কাবার্ডের এই দিকে, আর একটা হয়তো একেবারে ঐ দিকে।"
খানিকটা যেন গোয়েন্দা গল্পের ক্রাইম সিনের মত। তবে গোয়েন্দা গল্পে এই দৃশ্য থাকে প্রথম দিকেই, আর আমাদের এই কাহিনীতে এল সবার শেষে। দুজন মানুষ, যাঁরা কোনও এক সময়ে ভালবেসে বিয়ে করেছিলেন, এক ছাদের নিচে স্বামী স্ত্রী হয়ে বসবাস করতেন, তাঁরা এক সময়ে দেখলেন ভালবাসা তাঁদের ছেড়ে গেছে। এক সময়ে সেই ঘরও হয়ে উঠল ওয়েটিং রুমের মত, যেখানে তাঁরা অপেক্ষা করতেন কবে আসবে সেই অতি কাঙ্ক্ষিত বিচ্ছেদ। বিচ্ছেদ এল, তাঁরা ফের নতুন সাথীও পেলেন। তারপর এক দিন দেখা হল এক জংশন স্টেশনের ওয়েটিং রুমে। জংশন স্টেশন, যা দুই লাইনের সংযোগ ঘটায়; ওয়েটিং রুম, যেখানে মানুষ প্রতীক্ষা করে নতুন কিছুর, এমন কিছুর যা সেখানে আসার আগের আর পরের জীবনের মধ্যে কোনও সরু-মোটা পার্থক্য নিয়ে আসবে। রাজপুর জংশনের ওয়েটিং রুমেও ঠিক তাই হয়। কোথা থেকে যেন দু জন আসে, "তৃষ্ণা মিটিয়ে" চলে যায়। যতই কাঙ্ক্ষিত বিচ্ছেদ হোক, আমাকে বাদ দিয়ে অপর মানুষটি কেমন রয়েছে সেটা জানার তৃষ্ণা একটা স্বাভাবিক অনুভূতি। সেই তৃষ্ণা মেটে ওই স্টেশনে, তারপর… তার আর পর নেই। কেবল পাশাপাশি ছিল যে দুটো পেয়ালা, সে দুটোও হয়তো আর পাশাপাশি থাকবে না। ওয়েটিং রুমের কর্মচারী ভাল করে ধুয়ে দেবে কাপ, চিরকালের জন্য মুছে যাবে দু জন মানুষের ক্ষনিকের নৈকট্যের যাবতীয় চিহ্ন। তারা জায়গা পাবে কাবার্ডের দুই প্রান্তে, একে অন্যের থেকে দূরে। ঠিক ওই দু-জন মানুষের মত, যারা তৃষ্ণা মিটিয়ে চলে গেছেন দূরে, অনেক দূরে।
নিমগাছ - বনফুল
"নিমগাছটার ইচ্ছে করতে লাগল লোকটার সঙ্গে চলে যায়। কিন্তু পারলে না। মাটির ভেতর শিকড় অনেক দূরে চলে গেছে। বাড়ির পিছনে আবর্জনার স্তূপের মধ্যেই দাঁড়িয়ে রইল সে।
ওদের বাড়ীর গৃহকর্ম-নিপুণা লক্ষ্ণী বউটার ঠিক এই দশা।"
“বাবুমশায়, জিন্দগী বড়ি হোনি চাহিয়ে, লম্বি নহি,” হৃষিকেশ মুখার্জির ‘আনন্দ’ ছবিতে যে এই কথা বলেছিল তার আয়ু বেশি দিন ছিল না। আর সেটা তার জানাও ছিল। সেই স্বল্পস্থায়ী জীবন যা এক দিন সমুদ্রতীরে বিক্রি হওয়া বেলুনের মত শূণ্যে মিলিয়ে যাবে, তাকে নানা রঙে ভরিয়ে, নানা প্রাণে ছড়িয়ে দিয়ে বিস্তৃতি দিয়েছিল আনন্দ নামের ক্যান্সারের রোগীটি। যা ছোট, তা এই ভাবেই বিস্তার লাভ করে। সাহিত্যেও আমরা দেখি শেষের একটি লাইন কোথা থেকে এসে ক্ষুদ্র এক রচনাকে মহিমান্বিত করে তোলে। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ‘মেজাজ’ কবিতার সেই কৃষ্ণাঙ্গী বৌটিকে মনে আছে, গায়ের রঙের কারণে শাশুড়ির যাকে বিষনজরে দেখত। কবিতার শেষে জানা যায় সন্তানের নাম সে দিতে চায় ‘আফ্রিকা’, কারণ, “কালো মানুষেরা কী কাণ্ডই না করছে সেখানে”। বনফুলের ‘নিমগাছ’-ও সেই শ্রেনীতে পড়ে। নিমের ছাল, পাতা, ফল, সবই মানুষের প্রয়োজনে লাগে, কিন্তু তার নিজের উপকারে কেউ আসে না। প্রয়োজনের বাইরে তার আর কোনও মূল্য নেই। তবু সে কোথাও চলে যেতেও পারে না, পারবেও না। মাটিরে অনেক গভীরে চলে গেছে তার শিকড়। একটা আত্মকথা জাতীয় গল্প ঢিমে তেতালায় এগোতে এগোতে শেষ লাইনে এসে এমন উচ্চতায় পৌঁছে যায় যার তুলনা মেলা ভার। গল্পের ওজন তাতে বিস্তার লাভ করে, কিন্ত “ওদের বাড়ির গৃহকর্ম-নিপুণা লক্ষ্ণী বউটার” জীবনে কোনও বদল আসে না, আসবে না।
অঙ্গার - প্রবোধকুমার সান্যাল
"শোভনা কাঁদুক, সবাই কাঁদুক। আমি অসাড় ও অন্ধের মত হাতড়ে হাতড়ে সেখান থেকে বেরিয়ে সোজা বাইরে এসে পথে নামলুম। অন্ধকারে কোথাও কিছু দেখতে পেলুম না। শুধু অন্ধকার, অনন্ত অন্ধকার। কেবল মনে হলো, অঙ্গারের আগুন যেমন পুড়ে পুড়ে নিস্তেজ হয়ে আসে, তেমনি মহানগরের ক্ষুধাশ্রান্ত কাঙালীরা চারিদিকে চোখ বুজে পথে-ঘাটে নালা-নর্দমায় শুয়ে মৃত্যুর পদধ্বনি কান পেতে শুনছে!"
কান্না, অন্ধকার, মৃত্যু - কোন ইতিবাচক শব্দ নেই, কোনও আশার আলো দেখা যায় না অঙ্গার গল্পের শেষে। পূর্ব পাকিস্তানে যুদ্ধের সাথে সাথে ঢেউয়ের মত এসেছে সহায়সম্বলহীন মানুষ, সীমানা পেরিয়ে। যেভাবে যুদ্ধক্লান্ত মানুষ আজও এক দেশ থেকে অন্য দেশে পাড়ি দেয় - এক অজানা ভীতিকর ভবিষ্যৎ থেকে বাঁচতে অন্য এক অনিশ্চিতের দিকে, আইন-বেআইনের পরোয়া না করে। বুকের মাঝে এইটুকু আশা থাকে যে কিছু একটা… যে কোনও কিছু একটা... ঠিক হয়ে যাবে, জীবন ভাল কিছু নিশ্চয় দেবে। কেউ ভাল কিছু পায় বহু যন্ত্রণার পর, কেউ পায় না। আর এই পাওয়া বা না-পাওয়ার আগের সময়টুকু শুধুই অপমানের, পতনের আর মর্যাদাহানির। যেন তেন প্রকারেণ পেট চালানোই যখন একমাত্র তাগিদ, তখন "কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালবাসে"। জঠরের লেলিহান আগুন নেভানোর চেষ্টা চালিয়ে যেতে যেতে এক সময়ে হৃদপিণ্ড নামের অঙ্গারের ক্ষীণ আগুন নিভে আসে। তখন শুধু অন্ধকার, হাহাকার, কান্না আর নালা নর্দমার ধারে পড়ে থেকে মৃত্যু। আর এই কুৎসিত দগদগে নগ্ন ক্ষতের মাঝে পুঁজের মত বেরিয়ে থাকে একটি নাম - শোভনা।
তোতাকাহিনী - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
"পাখি আসিল। সঙ্গে কোতোয়াল আসিল, পাইক আসিল, ঘোড়সওয়ার আসিল। রাজা পাখিটাকে টিপিলেন, সে হাঁ করিল না, হুঁ করিল না। কেবল তার পেটের মধ্যে পুঁথির শুকনো পাতা খস্খস্ গজ্গজ্ করিতে লাগিল।
বাহিরে নববসন্তের দক্ষিণহাওয়ায় কিশলয়গুলি দীর্ঘনিশ্বাসে মুকুলিত বনের আকাশ আকুল করিয়া দিল।"
এ কাহিনী কবেকার? এ কি একশ তিন বছর আগে প্রকাশিত কোনও রচনা, না কি সদ্য লেখা হল? শিক্ষাঙ্গনের ভিতরে সুরক্ষা বাহিনী আর বোধহীন শাসক, আর বাইরে কিশলয়দের দীর্ঘশ্বাস - এ তো হাল আমলের কথা। গল্প শেষ হওয়ার খানিক আগেই নিন্দুকের কানমলার আদেশও দেওয়া হয়েছে। রূপরসহীন শুকনো কাঠের মত পাঠদানের ঊর্ধ্বে উঠে পড়ানোকে আনন্দময় করে তোলা শত বছরেও সম্ভব হল না। তবে হ্যাঁ, আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সৌন্দর্য বেড়েছে - হয়তো তার প্রয়োজনও আছে, সুরক্ষাও বেড়েছে। কিন্তু যার জন্য এত কাণ্ড, সেই পড়াশোনার কতটা উন্নতি হল আমাদের? আমরা তো সেই শুকনো পাতাই জাবর কেটে চলেছি, পরীক্ষার হলে তা উগড়ে দিচ্ছি, আর বিনিময়ে পাচ্ছি নম্বর, যা এখন বাড়তে বাড়তে আকাশছোঁয়া হয়েছে। ছাত্রছাত্রী খুশি, অভিভাবক খুশি, শিক্ষা দফতর আনন্দিত। আর কীই বা চাই? পড়াশোনায় মুক্ত চিন্তা, উত্তর রচনায় নিজস্বতাকে সম্মান দেওয়ার তো প্রয়োজন নেই। সুতরাং যা হওয়ার তাই হয়, বাইরের মুক্ত বাতাস ভিতরে প্রবেশ করতে না পেরে আকুল হয়ে ওঠে, আর আমরাও হাঁ-হুঁ না করে নীরব থাকি। আসলে যেন অনুভব করতে পারি যে ওই অকালমৃত পাখির মত আমাদের পেটের মধ্যেও পুঁথির শুকনো পাতা খসখস গজগজ করছে।
পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কিত নীতিঃ এই লেখাটি ছাপা, ডিজিটাল, দৃশ্য, শ্রাব্য, বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিলিপিকরণ বা অন্যত্র প্রকাশের জন্য গুরুচণ্ডা৯র অনুমতি বাধ্যতামূলক। লেখক চাইলে অন্যত্র প্রকাশ করতে পারেন, সেক্ষেত্রে গুরুচণ্ডা৯র উল্লেখ প্রত্যাশিত। - আরও পড়ুন'৪৭-এর সেই আগস্ট - Nirmalya Nagআরও পড়ুনবৈঠকি আড্ডায় ১৪ - হীরেন সিংহরায়
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
 বন্দনা রায় | 2402:3a80:ab3:18d9:0:58:ea88:501 | ০৯ নভেম্বর ২০২০ ০৭:৫৫99788
বন্দনা রায় | 2402:3a80:ab3:18d9:0:58:ea88:501 | ০৯ নভেম্বর ২০২০ ০৭:৫৫99788তুলনাহীন ।
 শেষ | 2600:1002:b004:1cf2:8414:32b1:588b:7589 | ০৯ নভেম্বর ২০২০ ০৮:৪৬99790
শেষ | 2600:1002:b004:1cf2:8414:32b1:588b:7589 | ০৯ নভেম্বর ২০২০ ০৮:৪৬99790আর পথের পাঁচালির শেষটা ?
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
-
গুরুচণ্ডা৯-র গ্রাহক হোন
কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে গুরুচণ্ডা৯-র গ্রাহক হোন। গুরুচণ্ডা৯তে প্রকাশিত লেখাগুলি পেতে চাইলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যুক্ত হোন, অথবা, আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলটির গ্রাহক হোন।
- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই
- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... )
(লিখছেন... )
(লিখছেন... অরিন, aranya)
(লিখছেন... kk, রমিত চট্টোপাধ্যায়, বিপ্লব রহমান)
(লিখছেন... Aranya )
- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন
(লিখছেন... Amit )
(লিখছেন... )
(লিখছেন... সৃষ্টিছাড়া, সমরেশ মুখার্জী)
(লিখছেন... দীপ, সুদীপ্ত, দীপ)
(লিখছেন... সমরেশ মুখার্জী, Kishore Ghosal, সমরেশ মুখার্জী)
- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... )
(লিখছেন... পাপাঙ্গুল)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... jsl)
(লিখছেন... অরিন, &/, অরিন)
- কি, কেন, ইত্যাদি
- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...
- আমাদের কথা
- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...
- বুলবুলভাজা
- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...
- হরিদাস পালেরা
- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...
- টইপত্তর
- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...
- ভাটিয়া৯
- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...
- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।
গুরুচণ্ডা৯-র সম্পাদিত বিভাগের যে কোনো লেখা অথবা লেখার অংশবিশেষ অন্যত্র প্রকাশ করার আগে গুরুচণ্ডা৯-র লিখিত অনুমতি নেওয়া আবশ্যক।
অসম্পাদিত বিভাগের লেখা প্রকাশের সময় গুরুতে প্রকাশের উল্লেখ আমরা পারস্পরিক সৌজন্যের প্রকাশ হিসেবে অনুরোধ করি।
যোগাযোগ করুন, লেখা পাঠান এই ঠিকানায় : [email protected] ।
মে ১৩, ২০১৪ থেকে সাইটটি
বার পঠিত