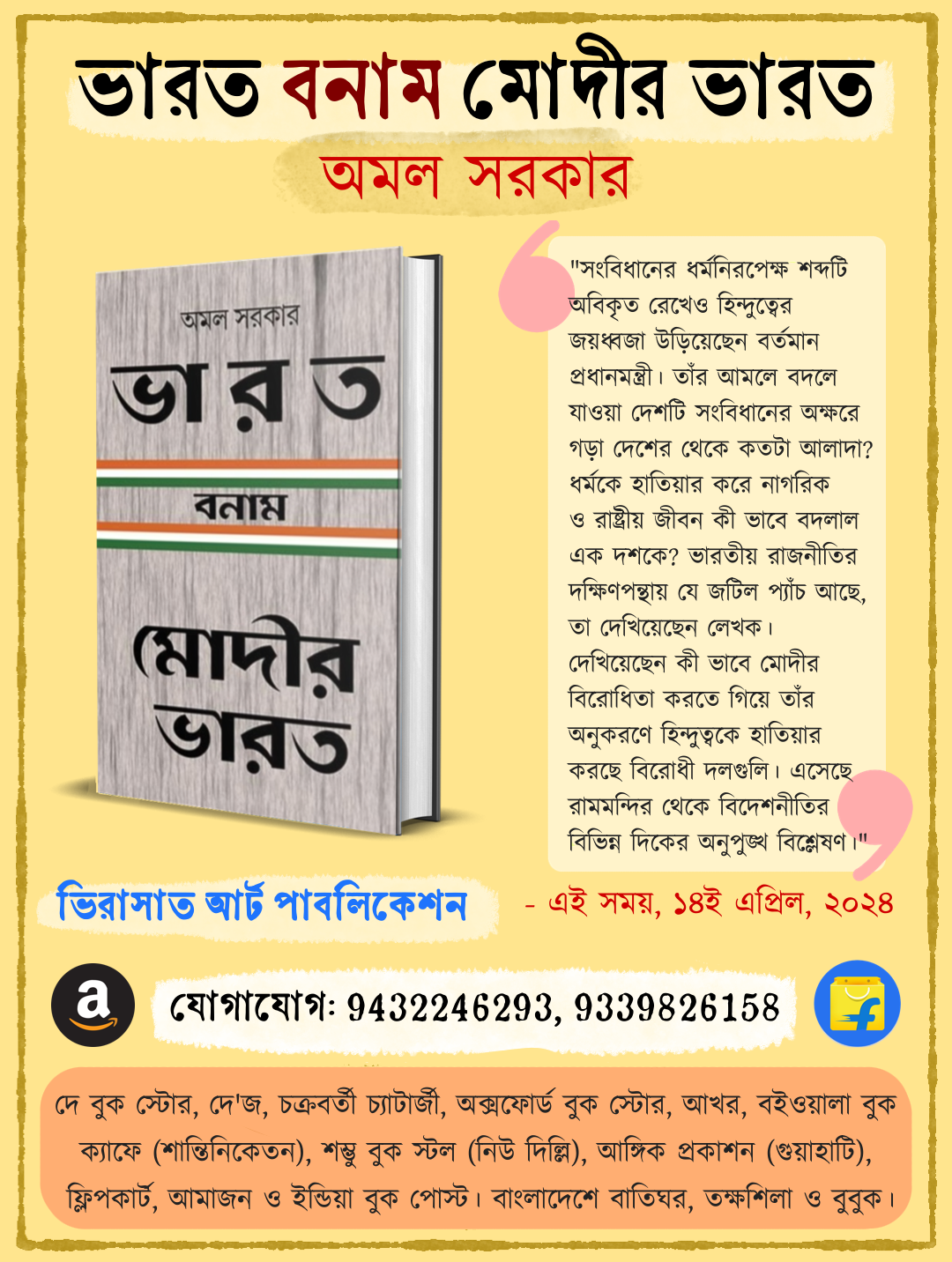- হরিদাস পাল আলোচনা শিক্ষা

-
(অন)লাইনের লেখাপড়া!
Sourav Mitra লেখকের গ্রাহক হোন
আলোচনা | শিক্ষা | ১২ অক্টোবর ২০২০ | ৩১৪০ বার পঠিত | রেটিং ৪.৫ (২ জন) - সময়টা ২০০২। তখন কলেজের বেশ কয়েকজন বন্ধুবান্ধবের মতো আমিও ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের পর এম.বি.এ. করার কথা ভাবছি। চাঁদা তুলে পোস্টাল কোচিং-এ এনরোলমেন্ট, জেরক্স করে স্টাডি মেটিরিয়াল ভাগ করা, দল বেঁধে পেপার সলভ্, গ্রুপ-ডিসকাসন চলছে। আর সেই সঙ্গে চাঁদা তুলে বিজনেস টুডে, ইত্যাদি পত্র-পত্রিকাও কেনা চলছে।
এই সব পত্র-পত্রিকায় মাঝেমধ্যেই দেশের বিজনেস স্কুলগুলোর র্যাঙ্কিং বেরোতো, যার প্রথম চার-পাঁচে (স্বাভাবিক ভাবেই) আই.আই.এম. আমেদাবাদ, ব্যাঙ্গালোর, কলকাতা, লখনউ-এর, তারপর এফ.এম.এস., এক্স.এল.আর.আই.-এর মতো কয়েকটি ইনস্টিটিউশানের নাম থাকতো। মজা শুরু হতো সাত-আট নম্বরের নামগুলো থেকে। র্যাঙ্কিংয়ে এরা আই.আই.এম. ইন্দোর বা কোজিকোরেরও ওপরে (বাকিগুলো তখনো তৈরি হয়নি), অথচ সেখানে ভর্তি হতে ক্যাটের বদলে ম্যাটের (অপেক্ষাকৃত কমা একটি এন্ট্রান্স টেস্ট) স্কোর থাকলেই চলে (না থাকলেও অসুবিধে হয় না)। সবারই টাই-ব্লেজার শোভিত ইউনিফর্ম আর (নাকি) ‘হান্ড্রেড পারসেন্ট প্লেসমেন্ট’! পরে চাক্ষুষ দেখেছি ওই কলেজগুলির বেশিরভাগেরই ক্যাম্পাসের মাপ বড়জোর বিঘেখানেক, লাইব্রেরি বলতে গোটা সাকুল্যে তিন-চারেক আলমারি, শিক্ষক বলতে কাছে-পিঠের কোনো নামকরা ম্যানেজমেন্ট কলেজ থেকে ধার করা পার্ট-টাইমার...। আসলে পশ্চিমবঙ্গ বা কর্ণাটকের স্যাকরা/ গোয়ালা/ প্রোমোটরদের তৈরি নিকৃষ্টতম প্রাইভেট ইঞ্জিনিারিং কলেজটির থেকেও খারাপ পরিকাঠামো!
তবে এদের সবাইকে ছাপিয়ে গিয়েছিল অরিন্দম চৌধুরী-খ্যাত দিল্লির আই.আই.পি.এম. নামের একটি কলেজ। সেই সময়ে শুরুতেই তারা প্রত্যেক ছাত্রকে ল্যাপটপ দিত (সেই সময়ে ল্যাপটপ আমাদের স্বপ্ন ছিল)। সেই সঙ্গে (নাকি) বিদেশের ইউনিভার্সিটির যৌথ ডিগ্রি, (নাকি) বিদেশে ইন্টার্নশিপ ও অস্থায়ী ওয়ার্ক-পারমিট, ইত্যাদি ইত্যাদি। সে’সময় যারা ভদ্রস্থ র্যাঙ্ক করে মোটামুটি পদস্থ কলেজে ভর্তি হয়েছিল তাদের অনেককেই পস্তাতে দেখেছি,- ‘ইশ্ যদি বাড়ির ফিনান্সিয়াল অবস্থা আরেকটু ভাল হতো, তাহলে-।’ সে এক দিন ছিল বটে! ততদিনে দেশের বিভিন্ন শহরে তাদের ক্যাম্পাস খোলা শুরু হয়ে গিয়েছে, চৌধুরীসাহেব একের পর এক মোটিভেশানাল বই লিখে চলেছেন, টিভিতে এসে দেশকে ‘ব্যাকডেটেড’ বলে খিস্তি করছেন, ইত্যাদি ইত্যাদি!
তারপর সেই আই.আই.পি.এম. প্রায় কুড়িহাজার ছাত্রের দুহাজারের কাছাকাছি মামলার মুখোমুখি হল।– মোটামুটি সবই প্রতারণার। একসময় ঝড় তোলা, ছাত্র-ছাত্রীর কোর্স-ফি দিয়ে বলিউডি সিনেমা অবধি বানিয়ে ফেলা ম্যানেজমেন্ট গুরু অরিন্দম চৌধুরী জেলের ঘানি অবধি টেনেছেন, তার কলেজও বন্ধ হয়েছে। (এমনকি যৌথ ডিগ্রির জন্য বেলজিয়ামের কলেজের সঙ্গে টাই-আপের কথা প্রচার করা হয়েছিল, সেই কলেজটির মালিক তিনিই, আর খোদ বেলজিয়ামে সেই কলেজের কোনো মান্যতাও ছিল না)।... তবে আরো অনেক মেজো-সেজো-ছোট চৌধুরীর কপাল ততটা খারাপ হয়নি। তারা ও তাদের কলেজগুলি আজও বহাল তবিয়তেই ঝুড়ি-ঝুড়ি এম.বি.এ. উৎপাদন করে চলেছে। (তবে বেশ কয়েকটি কলেজ অবশ্য বলার মতো উন্নতিও করেছে।)
কিন্তু প্রশ্ন হল, ওই সময়টায় একের পর এক ম্যানেজমেন্ট কলেজ খোলার বা তাদের ‘পেইড্-রিভিউ’ প্রকাশের এমন কী কারণ ছিল?- উত্তর: মধ্যবিত্ত ও মধ্যমেধা। ১৯৯১-এর উদারীকরণের বয়স তখন এক দশক। আমাদের মতো যারা ছাত্র, তাদের প্রত্যেকেরই কোনো না কোনো ‘তুতো’ দাদা আমেরিকায় বা ইংল্যান্ডে চাকরি করে, দেশেও বাবার আবসরের বছরের মাইনের সমান স্যালারি প্যাকেজ নিয়ে ছেলে-মেয়েরা চাকরিজীবন শুরু করছে। হর্ষদ মেহেতা বা কেতন পারেখ জাতীয় দু-একটা ঝটকা খেলেও অর্থনীতির চাকা তখন ভালই দৌড়চ্ছে।... মোট কথা যে সৎপথে বিলাসব্যসন তার আগে উচ্চবিত্ত আর উচ্চমেধাবীদের জন্যই বরাদ্দ ছিল (ও বাকিরা সেই বাস্তবতা মেনেও নিয়েছিল), তখন সে-সব হাতের নাগালে আসতে শুরু করেছে। ওই কলেজগুলো তখন স্বপ্নপূরণের মসিহা, তাদের টিউসান ফি থাকত দুই থেকে ছ’লাখের মধ্যে। অর্থাৎ সেই সময়ের একজন মধ্যবিত্ত চাকরিজীবীর পক্ষে নিজের প্রভিডেন্ট ফান্ড ভেঙে বা এডুকেশান লোন নিয়ে যা চোকানো সম্ভব।
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি সেদিনের এই ম্যানেজমেন্ট ছাত্রদের সিংহভাগ আজ পেশাগত ভাবে উচ্চ-মধ্য-নিম্ন যে অবস্থানেই থাকুক না কেন, সেই কৃতিত্ব বা ব্যর্থতায় তাদের ম্যানেজমেন্ট কলেজ বা ম্যানেজমেন্ট শিক্ষার ভূমিকা নেহাৎই গৌণ।... বলাই বাহুল্য, এই মধ্যবিত্ত-মধ্যমেধাবীদের আকাঙ্খাপূরণের ব্যাবসা শুধু ম্যানেজমেন্ট কলেজগুলোতেই সীমাবদ্ধ ছিল না।
তারপর দুটো দশক কেটেছে। সেদিনের ছাত্র-ছাত্রীরা আজ সন্তানের বাবা-মা । পেশাগত দিক থেকেও তারা প্রতিষ্ঠিত।– আগের প্রজন্মের তুলনায় তাদের রোজগারও বেশি। কিন্তু, আমার মতো এই মধ্যমেধাবীদের (মুখে প্রকাশ করি বা না করি), একটা গভীর ক্রাইসিস আছে।– উচ্চমেধা আর মধ্যমেধার পার্থক্য আমরা হাড়েহাড়ে জানি। আর এটাও জানি, ‘লেখাপড়ার ভিত মজবুত নাহলে পরে সমস্যা হয়’।– আর সেই সঙ্গে (মাত্রায় কিছু তারতম্য থাকলেও) প্রত্যেকেই বিশ্বাস করি, আমার ‘ঠিক যতটা ভেবেছিলাম ততটা না হওয়া’র কারণ কোনোভাবেই নিজের বুদ্ধিমত্তার সীমাবদ্ধতা নয়, শুধুমাত্র প্রস্তুতির ঘাটতি!
মধ্যবিত্তের এই ক্রাইসিসটাই এখন নতুন ব্যাবসাক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। মুঠোমুঠো প্রাইভেট স্কুল খুলতে শুরু হওয়া (যার অনেকগুলিরই মালিকানা ওই ম্যানেজমেন্ট কলেজগুলির ডিরেক্টারদের হাতেই) যদি এই সেই ব্যাবসার একটা দিক হয়, অন্য দিকটা হল প্যারালাল স্কুলিং। জয়েন্ট এন্ট্রান্সের প্রস্তুতির জন্য কোটা বা কানপুরের টিউশান নয়ের দশকেও ছিল, সেখানে মাফিয়ারাজও ছিল, এমন বহু কোচিং সেন্টারও ছিল যেখানে ভর্তি হতে চাইলে প্রথমে তাদের এন্ট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করতে হতো, কিন্তু এখন যেমনধারা চল হয়েছে,- অর্থাৎ যে পরীক্ষায় দ্বাদশ শ্রেণীর পর বসতে হয়, কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা খরচ করে অষ্টম শ্রেণী থেকেই তার প্রস্তুতি নেওয়ার কথা সেই সময়ের টপ র্যাঙ্কাররাও ভাবত বলে মনে হয় না।
প্যারালাল স্কুলিংয়ের এই ধারাটাও মোটামুটি একদশকের পুরোনো। এখন আর অষ্টম শ্রেণী নয়, প্রি-প্রাইমারি থেকেই তা শুরু হয়ে যাচ্ছে।– অনলাইনে বা মোবাইলেও। বাচ্চাগুলোর মানসিক বিকাশ-টিকাশের মতো ‘ঘ্যানঘ্যানে-প্যানপ্যানে’ বিষয় আলোচনার বাইরে রেখেই ভেবে দেখুন, অমন এক-একটি অনলাইন স্কুলের কী পরিমাণ টার্নওভার হলে বলিউডের ওপরদিকের নায়ক/ নায়িকা তার ব্র্যান্ড-অ্যাম্বাসাডার হয়, বা তারা একের পর এক আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সহ-স্পনসর ও বিশ্বের অন্যতম ধনী একটি ক্রীড়াসংস্থার মূখ্য-স্পনসর হয়ে উঠতে পারে!- কোত্থেকে আসে এই টাকা? কীসের বিনিময়ে?- চলুন, তার বৈষয়িক দিকটাই দেখা যাক।
প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণী অবধি মোটামুটি বছরে পঞ্চাশ হাজার টাকা করে কোর্স ফি। সেখানে আবার ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের ধাঁচেই একসঙ্গে তিনবছরের বেতন দিলে পঁচিশ-তিরিশ শতাংশ ছাড়! চতুর্থ থেকে দশম শ্রেণী অবধি (শুধু অঙ্ক ও বিজ্ঞানের জন্য) প্রতিবছর তিরিশ-চল্লিশ হাজার টাকা। একাদশ-দ্বাদশে এসে সত্তর হাজার থেকে দু’লাখ টাকার বিভিন্ন প্যাকেজ, তার সঙ্গে মক্-টেস্ট, ক্রাশ-কোর্স বাবদ আরো হাজার-পঞ্চাশেক টাকা।...
এই ছয়-সাত লাখটাকা খরচ করার পর অভিভাবক হিসেবে আপনি কী কী পাবেন?- শুরুতেই একটি ল্যাপটপ, আর তারপর ‘ও তো বেশ মেধাবী, কিন্তু...’, ‘ও তো খুবই পরিশ্রম করছে, কিন্তু...’, ‘আমরা সবরকম চেষ্টাই করছি, কিন্তু...’। বলাই বাহুল্য, এই বেশিরভাগ সময়েই এই ‘কিন্তু’গুলোর রহস্যের সমাধান হবে না। তবে আপনার ছেলে বা মেয়ে প্রথম চেষ্টায় জয়েন্ট উৎরোতে না পারলে দ্বিতীয়বার নাম নথিভুক্ত করানোর সময় সেই পঁচিশ-তিরিশ শতাংশের ছাড় পেতেই পারেন। আর হ্যাঁ, প্যাথোলোজিক্যাল ল্যাবগুলোর যেমন অনেক ডাক্তারের সঙ্গে বোঝাপড়া থাকে, ঠিক তেমন ভাবে এই সংস্থাগুলো বহু শিক্ষককেই ‘ধরে রাখে’। ফলে পরামর্শ ও সৎ-পরামর্শের তফাৎ করাও কঠিন হয়ে যায় মাঝেমাঝে।
দয়া করে ভুল ভাববেন না, এত খেদোক্তি মানুষের আকাঙ্খা বা পরীক্ষার প্রস্তুতির বিরুদ্ধে নয়, সেগুলিকে ঘিরে গজিয়ে ওঠা ‘অনৈতিক’ ও অমানবিক ব্যাবসার প্রতি। শাহজাদ ফিরদৌসের ‘ব্যাস’ উপন্যাসে একটি অসাধারণ কথা ছিল,- লোভ-কে আকাঙ্খা আর ভোগ-কে প্রাপ্তি ভাবাটা ভুল।... মধ্যবিত্ততা বা মধ্যমেধা কোনো অভিশাপ বা কলঙ্ক নয়, যা যে কোনো মূল্যে তা ধুয়ে ফেলতে হবে। ভেবে দেখার বিষয় হল, ওপরের অনুচ্ছেদগুলোয় যার বর্ণনা করা হয়েছে, তাকে কোনো দিক থেকেই ‘শিক্ষা’ বলা যায় কী?...
পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কিত নীতিঃ এই লেখাটি ছাপা, ডিজিটাল, দৃশ্য, শ্রাব্য, বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিলিপিকরণ বা অন্যত্র প্রকাশের জন্য গুরুচণ্ডা৯র অনুমতি বাধ্যতামূলক। লেখক চাইলে অন্যত্র প্রকাশ করতে পারেন, সেক্ষেত্রে গুরুচণ্ডা৯র উল্লেখ প্রত্যাশিত। - আরও পড়ুনঘর-গেরস্থালি (৩) - Sourav Mitraআরও পড়ুনঘর-গেরস্থালি (২) - Sourav Mitraআরও পড়ুনঘর-গেরস্থালি (১) - Sourav Mitraআরও পড়ুনরাতপরী (গল্প) - Sourav Mitraআরও পড়ুনবৈঠকি আড্ডায় ১৪ - হীরেন সিংহরায়আরও পড়ুনহন্য - সৈয়দ তৌশিফ আহমেদআরও পড়ুনটুনিমুনির জীবন - দময়ন্তীআরও পড়ুনকোশিশ কিজিয়ে - কিশোর ঘোষালআরও পড়ুনজুমলা যখন - সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায়
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
 r2h | 165.1.200.98 | ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ০২:৪৯523673
r2h | 165.1.200.98 | ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ০২:৪৯523673- এই লেখাটা হঠাৎ চোখে পড়লো। তুলে রাখি।
শিক্ষা ব্যবসা, শিক্ষার ধরন, লক্ষ্য - এই জিনিসগুলি নিয়ে আলোচনা সব সময়ই প্রাসঙ্গিক। তার ওপর কোভিডের পর আবার আরেক রকম হয়েছে।
 &/ | 151.141.85.8 | ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ০২:৫৮523674
&/ | 151.141.85.8 | ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ০২:৫৮523674- বাহ, বাহ, দারুণ লেখা। যাকে বলে, ব্যাপার গুরুচরণ!
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
-
গুরুচণ্ডা৯-র গ্রাহক হোন
কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে গুরুচণ্ডা৯-র গ্রাহক হোন। গুরুচণ্ডা৯তে প্রকাশিত লেখাগুলি পেতে চাইলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যুক্ত হোন, অথবা, আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলটির গ্রাহক হোন।
- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই
- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... )
(লিখছেন... )
(লিখছেন... অরিন, aranya)
(লিখছেন... kk, রমিত চট্টোপাধ্যায়, বিপ্লব রহমান)
(লিখছেন... Aranya )
- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন
(লিখছেন... Amit )
(লিখছেন... )
(লিখছেন... সৃষ্টিছাড়া, সমরেশ মুখার্জী)
(লিখছেন... দীপ, সুদীপ্ত, দীপ)
(লিখছেন... সমরেশ মুখার্জী, Kishore Ghosal, সমরেশ মুখার্জী)
- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... )
(লিখছেন... পাপাঙ্গুল)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... jsl)
(লিখছেন... অরিন, &/, অরিন)
- কি, কেন, ইত্যাদি
- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...
- আমাদের কথা
- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...
- বুলবুলভাজা
- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...
- হরিদাস পালেরা
- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...
- টইপত্তর
- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...
- ভাটিয়া৯
- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...
- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।
গুরুচণ্ডা৯-র সম্পাদিত বিভাগের যে কোনো লেখা অথবা লেখার অংশবিশেষ অন্যত্র প্রকাশ করার আগে গুরুচণ্ডা৯-র লিখিত অনুমতি নেওয়া আবশ্যক।
অসম্পাদিত বিভাগের লেখা প্রকাশের সময় গুরুতে প্রকাশের উল্লেখ আমরা পারস্পরিক সৌজন্যের প্রকাশ হিসেবে অনুরোধ করি।
যোগাযোগ করুন, লেখা পাঠান এই ঠিকানায় : [email protected] ।
মে ১৩, ২০১৪ থেকে সাইটটি
বার পঠিত