-
বুলবুলভাজা
-
এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়।
বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচণ্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। - গুরুভার আমার গুরু গুরুতে নতুন? বন্ধুদের জানান
- সময়ানুক্রমে | সদ্য আলোচিত | মন্তব্য অনুসারে | পঠিত অনুসারে | লেখক তালিকা
-
- নতুন আলোচনা
-
বিষয়ের শিরোনাম*:বিষয়বস্তু*:
- পাতা : ২৪১২৪০২৩৯২৩৮২৩৭২৩৬২৩৫২৩৪২৩৩২৩২

HIV /AIDS Act, ২০১৭ ও কিছু কথা - Jaydip
বুলবুলভাজা | আলোচনা : স্বাস্থ্য | ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ | ৭৯১ বার পঠিত | মন্তব্য : ৪, লিখছেন (kk, ইন্দ্রাণী, Amit tor friend (RBU))বহু প্রতীক্ষার পর যখন ২০১৭ তে এসে এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তিদের মানবাধিকার রক্ষার জন্য তৈরী হওয়া এইচআইভি ও এইডস আইন ২০১৭ পাশ হয়েছে। এই আইন সারা দেশে ১০ই সেপ্টেম্বর ২০১৮ থেকে কার্যকর করা শুরু হয়ে গেছে। চলুন সংক্ষেপে জেনে নিই কি বলছে আইন... ... ...
গদ্য সাহিত্যের অনুবাদ প্রসঙ্গে আশীষ লাহিড়ীর সঙ্গে খোলামেলা আড্ডাঃ পর্ব ২ - রূপক বর্ধন রায়
বুলবুলভাজা | আলোচনা : বিবিধ | ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ | ১১৪১ বার পঠিত | মন্তব্য : ৩, লিখছেন (শুদ্ধসত্ত্ব দাস, Mantu Lahiri, রূপক বর্ধন রায়)সে যাই হোক, তোমায় একটা আবিষ্কারের গল্প বলি শোনো। এসব কথায় কথায় উঠে আসে। সুগতবাবু রবীন্দ্রনাথকে নানান জায়গায় কোট করেছেন ওঁর বইতে, তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিকতা বা কট্টর-জাতীয়তাবাদ-বিরোধিতা ইত্যাদির উপর জোরও দিয়েছেন। তো এক জায়গায় ১৮৯৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বরে নতুন শতাব্দীর সময়টাকে ধরতে গিয়ে উনি রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতাটা কোট করছেন, 'শতাব্দীর সূর্য আজি রক্তমেঘ মাঝে অস্ত গেল'। এইটা দিয়ে উনি তখনকার পরিস্থিতিটাকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছেন, যে কেন রবীন্দ্রনাথ এটা লিখলেন। এইটারই আবার রবীন্দ্রনাথের করা একটা অনুবাদ ন্যাশনালিজম বইয়ের পরিশিষ্টে আছে। তো আমি রবীন্দ্রনাথের বাংলাটা আর ইংরেজিটা মেলাতে গিয়ে দেখলাম ইট ইজ এ রেভিলেশান। কারণ প্রথম লাইনগুলো হুবহু এক, কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু তারপর দেখি কবিতার লাইন আর মিলছে না। আবার কয়েকটা লাইনে দেখি নাহ এই কবিতা থেকেই নেওয়া, খানিক দূর যাওয়ার পর দেখি আবার মিলছে না! ইংরেজি কবিতাটা বেশ বড়, আর বাংলাটা ততটা বড় নয় কারণ ওটা সনেট- ১৪ লাইনের। বাংলাটা লেখা হয়েছিল ১৮৯৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর, আর উনি ওটার ইংরেজি করছেন ১৯১৩ কি ১৪ সালে- যদ্দূর সম্ভব; কাজেই ততদিনে তার মধ্যে কিছু পরিবর্তন এসেছে। ... ...
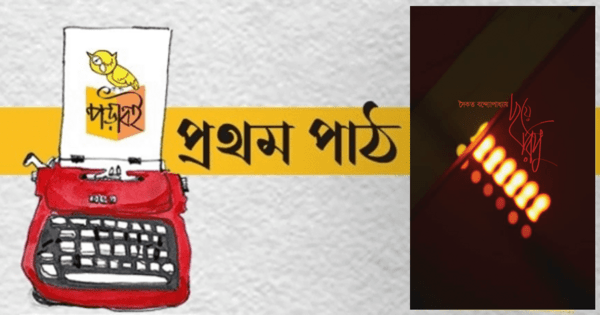
ছয়ে রিপু – পাঠ-প্রতিক্রিয়া - শুভদীপ ঘোষ
বুলবুলভাজা | পড়াবই : প্রথম পাঠ | ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ | ১৮৫৪ বার পঠিত | মন্তব্য : ৭, লিখছেন (ইন্দ্রাণী, Sobuj Chatterjee, গ্রন্থটি কিভাবে)'এই ধরনের অপরাধে সেদিনই ছিল আমার হাতেখড়ি, যেজন্য বিপদটা হল।...' (শীতবন্দরে)। 'গোলমালটা ঠিক কীভাবে শুরু হল বলা খুব কঠিন।..' (পাইথনের গপ্পো)। 'কেলোটা হল বড়দিনে।...' (বড়দিন)। 'আবহাওয়ার পূর্বাভাসে ঝড় আসার কথাই ছিল।...'(ক্যাম্পফায়ার, আমাদের রাতের উৎসব)। এই জাতীয় সূচনা লেখকের একটি বিশেষ স্টাইল। শুরুর এই কৌতূহল না মেটা পর্যন্ত পাঠক স্বস্তি পাবেন না। কিন্তু চিত্তাকর্ষক হল সেটা মিটে যাওয়ার পরে পাঠক টের পাবেন অতিরিক্ত কি একটা যেন বলা হল, যা প্লটের চাইতেও বেশি করে বেরিয়ে আসছে লেখকের অননুকরণীয় নির্মাণকৌশল থেকে! ... ...

পূর্ব ইউরোপের ডায়েরি – কাজাখস্তান ৬ - হীরেন সিংহরায়
বুলবুলভাজা | ধারাবাহিক : ইতিহাস | ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ | ১৩২৫ বার পঠিত | মন্তব্য : ৫, লিখছেন (Kishore Ghosal, Debanjan Banerjee, হীরেন সিংহরায়)বিগত তিরিশ বছরে নানান দেশের নানান ব্যাঙ্কিং প্যানেলে বহু জ্ঞানীগুণীর সঙ্গে একাসনে বসে ঘণ্টাখানেক বাক্যালাপ করে পাঁচজনের সঙ্গে আমিও ফিরিতে হাততালি কুড়িয়েছি। এইসব প্যানেল আমারই মত অন্যান্য ব্যাঙ্কের ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্কিঙের ফিরিওলা, কর্পোরেট প্রধান, সরকারি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মাঝারি প্রবক্তা, খবরের কাগজের প্রতিনিধি (যাঁরা প্রশ্ন করেন কেতাবি, উত্তরের অর্থ অর্ধেক বোঝেন কিনা সন্দেহ) এমনি সব মানুষদের নিয়ে তৈরি হয়। নির্ধারিত অনুষ্ঠানের আগেই আমরা কনফারেন্স কল (জুম কল আসতে দেরি আছে) করে ঠিক করে নিই প্রশ্নাবলী কী হবে, কে কী বলবে। শ্রোতারা ভাবেন – চার-পাঁচ জন নারী পুরুষ একত্র বসে কোনো অর্থনৈতিক সমস্যা বা বিষয়ের ওপরে কোনো গভীর তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ দ্বারা মহতী সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছেন। ... ...

সীমানা - ২৩ - শেখরনাথ মুখোপাধ্যায়
বুলবুলভাজা | ধারাবাহিক : উপন্যাস | ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ | ১৮৮৪ বার পঠিতভালো লাগে না কাজির, সে স্বভাবতই খোলামেলা চরিত্রের মানুষ, এই-যে দুলির সঙ্গে এমন একটা ঘনিষ্ঠতার সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ল সে, সেটাকে যে যথাসাধ্য গোপন করার চেষ্টা করতে হচ্ছে, এ তার ভালো লাগে না। কিন্তু গোপন না করেই বা কী উপায়? দুলি তো একেবারেই ছেলেমানুষ; নিজের ভালো যদি নিজে সে বুঝত! কাজির মতো একজন ছন্নছাড়া বিষয়আশয়হীন গৃহহীন অর্থসংস্থানহীন মানুষের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার অর্থ যদি সে বুঝত! বোঝে না, তাই কাজির দায়িত্ব আরও বেড়ে যায়। কিন্তু কাজির যে চিৎকার করে সারা পৃথিবীকে জানাতে ইচ্ছে করছে! ছন্নছাড়া হতে পারি, কিন্তু আমার মতো ভাগ্যবান কে আছে! ... ...

রসুইঘরের রোয়াক (দ্বিতীয় ভাগ) - ১৮ - স্মৃতি ভদ্র
বুলবুলভাজা | খ্যাঁটন : খানা জানা-অজানা | ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ | ১১৬৭ বার পঠিত | মন্তব্য : ৩, লিখছেন (R.K, Dipak Das, গোপা মুখোপাধ্যায়)সারাদিনের মধ্যে এই ফুলতোলার সময়টুকুতেই তো ঠাকুমাকে আমি আমার মতো করে পাই। এ-কথা ও-কথায় আমরা দু-জনকে বারবার জানাই—আর কেউ না, তুমিই আমার সব আবদারের জায়গা। তবে শহরে যাবার পর অবশ্য ঠাকুমার আবদার আমার থেকেও বেড়ে গেছে। ফুলের সাজি হাতে বাইরবাড়িতে যেতে যেতেই ঠাকুমার আবদার, ও দিদি, এবার বার্ষিক পরীক্ষায় খুব ভালো করতে হবে কিন্তু তোমার। শহরে বাবা নিয়ে গেছে তো ভালো করে পড়াতে। বাবার কথা মানতে হবে দিদি। ... ...

পাকশালার গুরুচণ্ডালি (৬০) - শারদা মণ্ডল
বুলবুলভাজা | খ্যাঁটন : হেঁশেলে হুঁশিয়ার | ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ | ৯৫২ বার পঠিত | মন্তব্য : ৪, লিখছেন (Sara Man, Shrabani Majumdar, Sara Man)— তোর ঠাকুরদার জন্ম ১৯২৩ সালে। ঐ সময়ে বাংলার অবস্থাটা আগে মন দিয়ে বোঝ। অমর যখন সাত বছরের বালক, তখন ঘরের পাশে পিছাবনিতে হয় লবণ সত্যাগ্রহ। — আরে পিছাবনি দিয়ে যখন আমাদের গাড়ি ঢোকে, তখন বাজারে ইস্কুলের কাছে একটা স্তম্ভ আছে, সেইটা? বাবা বারবার দেখায়? — হাঁ সেইটাই ঐ সত্যাগ্রহের স্মারক স্তম্ভ। জেলাশাসক পেডির সামনে মিছিল থেকে আওয়াজ উঠেছিল, ‘আমরা পিছাবনি’। — তারপর? ... ...
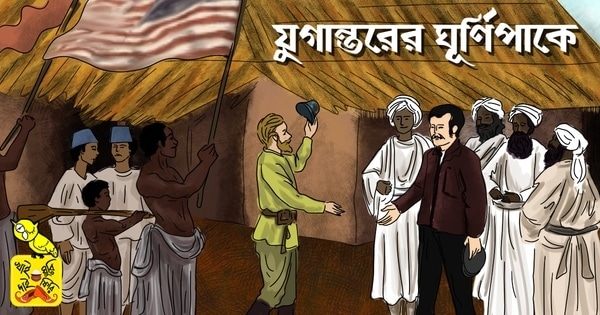
ডেভিড লিভিংস্টোনের খোঁজে-১০৯ - হেনরি মর্টন স্ট্যানলে
বুলবুলভাজা | ভ্রমণ : যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে | ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ | ৫৭৪ বার পঠিতউজিজি থেকে রওনা হওয়ার নবম সকালে মুগেরের বিস্তৃত ব-দ্বীপ পেরিয়ে গেলাম। সূর্যোদয়ের প্রায় দু ঘণ্টা পরে। মুগেরে নদীর নামেই মুকাম্বা শাসিত পূর্ব দিকের এলাকার নাম। এর তিনটে মুখের দক্ষিণতমটির সামনে এসে দেখলাম জলের রঙটা বেশ আলাদা। নদীর মুখ থেকে পূর্ব-পশ্চিমে একটা প্রায় সোজা দাগ কাটলে দুপাশের জলের রঙের পার্থক্য বেশ চেনা যাবে। দাগের দক্ষিণ দিকে হালকা সবুজ বিশুদ্ধ জল, আর উত্তরে কাদাঘোলা জল, উত্তরমুখো স্রোত স্পষ্ট দেখা যায়। প্রথম মুখটি অতিক্রম করার পরপরই দ্বিতীয় মুখের কাছে পৌঁছলাম আর তারপরেই তিন নং মুখের কাছে এসে পড়লাম, সব কটাই মাত্র কয়েক গজ চওড়া, কিন্তু প্রতিটা স্রোতধারাই পর্যাপ্ত জল বয়ে আনছে । ফলে আমরা সংশ্লিষ্ট নদী মুখের থেকে অনেকটাই উত্তরে, জলের স্রোত বরাবর চললাম। ... ...
গদ্য সাহিত্যের অনুবাদ প্রসঙ্গে আশীষ লাহিড়ীর সঙ্গে খোলামেলা আড্ডাঃ পর্ব ১ - রূপক বর্ধন রায়
বুলবুলভাজা | আলোচনা : বিবিধ | ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ | ১২৬৪ বার পঠিত | মন্তব্য : ৫, লিখছেন (প্রতিভা, sch, শুভময় দত্ত। )প্রথমত, কবিতা ব্যাপারটাই, মানে সেই রবীন্দ্রনাথের কথায়, ফুলের গন্ধের মত। ব্যাপারটা কী ইউ ক্যানট ডিফাইন। মানে এই অস্পষ্টতাটাই কবিতার বৈশিষ্ট্য। আমি যেমন কবিতা একেবারে লিখতে পারি না। একসময় রবীন্দ্রনাথের কিছু গান বা কবিতা অনুবাদের চেষ্টা করেছি। আমার ভাই সৌমিত্রও করতো, আমারা একে অপরের সঙ্গে মেলাতাম; কিন্তু আমি দেখেছি যে আমার হাতে সেটা প্যারাফ্রেজিং হয়ে যাচ্ছে। মানে সেটা পড়ে মূল কবিতার অর্থটা বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু দ্যাট ইজ নট দি পোয়েম। কাজেই কবিতার ক্ষেত্রে ওই যে এক্সট্রা মাত্রাটা, সেটা শুধু তার লজিক নয়, শুধু তার শব্দ নয়, অথবা সবকিছু মিলিয়ে, ধরো তার ধ্বনি, মানে এই সবকিছু মিলিয়ে যে বাড়তি ব্যাপার, আমার মনে হয় অনুবাদে সেটা সম্ভবই না। তাহলে কি বলবে কবিতা অনুবাদের কোনো মানে নেই? এক অর্থে হয়তো নেই! রবীন্দ্রনাথ নিজেই তার প্রমাণ। কোনো কোনো নির্দিষ্ট জায়গায় ইংরেজি গীতাঞ্জলি বেশ ভালো, তাতে কোনো সন্দেহ নেই! কিন্তু যারা গীতাঞ্জলিকে বাংলা-গীতাঞ্জলি হিসেবে পড়েছে তারা সেই রসটা খুঁজে পাবে না। অর্থাৎ যে লোক বাংলা জানে না তার কাছে কিন্তু ওটার মূল্য আছে এবং সেখানেই আমি বলবো কবিতা অনুবাদের সার্থকতা; যেটা বুদ্ধদেব বসুও পয়েন্ট আউট করেছিলেন। ... ...

ঘ্যাঁক করার পরে - অম্লানকুসুম চক্রবর্তী
বুলবুলভাজা | অন্যান্য | ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ | ২৭৭৬ বার পঠিত | মন্তব্য : ৫৭, লিখছেন (দারুন লেখক ????, dc, রমিত চট্টোপাধ্যায়)পুষে রাখা সারমেয়র যত্ন কিভাবে করা যায়, তা নিয়ে প্রায়ই পড়ি খবরের কাগজে। কালীপুজোর রাতে বাজির প্রবল আওয়াজে বাড়ির কুকুরটি যেন ভয় না পায়, জানালার সামনে মাইক বাজিয়ে ডিজে সঙ্গীত হলে প্রিয় সারমেয়টি যেন আতঙ্কিত না হয়, তা নিয়ে বহু টোটকা দেন পশু বিশেজ্ঞরা। হৃদযন্ত্রের সমস্যার ভোগা আপনার মানুষ-প্রিয়জনকে এই অত্যাচারের হাত থেকে থেকে কিভাবে নিরাপদ রাখা যায়, তার তুলনায় অনেক বেশি নিউজপ্রিন্ট খরচ হয় পোষ্যের যত্নের সন্ধানে। কিন্তু ঘরে পুষে রাখা অবাধ্য পশুকে কিভাবে লাগাম দিতে হয়, তা নিয়ে চোখে পড়ে না কিছু। অন্যের শরীরে দাঁত বসিয়ে দিলেও দিনের শেষে সেই সারমেয় ‘অবলা’ই থেকে যায়। ... ...
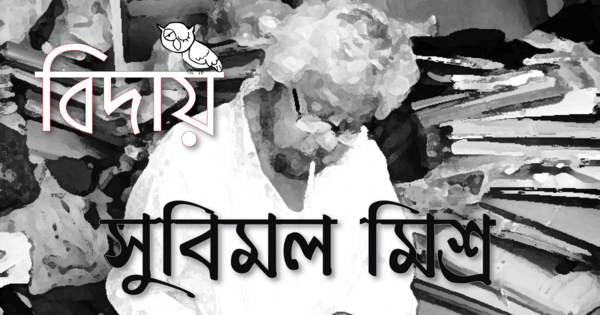
বিদায় সুবিমল মিশ্র - অমর মিত্র
বুলবুলভাজা | স্মৃতিচারণ | ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ | ২৭৭৩ বার পঠিত | মন্তব্য : ১৭, লিখছেন (Jayati roy , তাপস হালদার, সঞ্জীব দেবলস্কর )পদবী-বর্জিত সুবিমলমিশ্র কোনোদিন একটি বর্ণও কোনো প্রাতিষ্ঠানিক পত্রিকায় লেখেননি। আমি তাঁকে পড়েছি লিটল ম্যাগাজিনে। সুবিমল কোনোদিন সাহিত্যের প্রতিষ্ঠান, একাডেমির কাছ দিয়ে হাঁটেননি, আমি তাঁকে পড়েছি মানিক তারাশঙ্কর পড়তে পড়তে নিজ প্রয়োজনে। তাঁর লেখার ভিতরে যে ঝাঁজ দেখেছি সেই চল্লিশ বছর আগে, তা আমাকে শিখিয়েছিল অনেক। আমি নিজে সুবিমলের সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রেই সহমত নই, তাঁর পথ আর আমার পথ আলাদা কিন্তু দূরে থেকেও আমি তাঁর লেখার অনুরাগী। ... ...
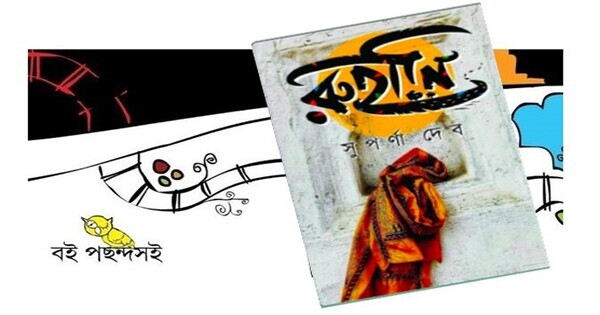
রুহানি - প্রতিভা সরকার
বুলবুলভাজা | পড়াবই : বই পছন্দসই | ৩১ জানুয়ারি ২০২৩ | ১৩৪৫ বার পঠিত | মন্তব্য : ৪, লিখছেন (শিবাংশু, মোহাম্মদ কাজী মামুন, Ranjan Roy)এ এক অদ্ভুত বই। পাতার পর পাতা উলটেও আমি ঠিক করতে পারিনি এ কোন বৃক্ষের ফুল, কোন জনরেঁ এর উৎস। প্রবন্ধ, ইতিহাস, রসনা-রেসিপি, ইদানীং ফুড-ব্লগ নামে যা জগত-বিখ্যাত, শিল্প ও শিল্পীর ওপর কিছু কথা, নাকি কেবলই মনোহরণ দাস্তান বা আখ্যানগুচ্ছ। সব কাননের ফুলের সুবাস পাওয়া যাবে এতে আলাদা করে, আবার প্রত্যেকটি মিলেমিশে একটি নিবিড় কথকতা! বাংলা সাহিত্যে এরকম আর কিছু আছে কি? ... ...
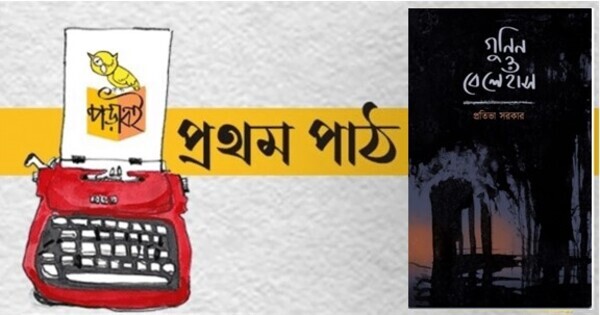
গুনিন ও বেলেহাঁস - পাঠ প্রতিক্রিয়া(১) - স্বাতী রায়
বুলবুলভাজা | পড়াবই : প্রথম পাঠ | ২৯ জানুয়ারি ২০২৩ | ১০৩৩ বার পঠিত | মন্তব্য : ২, লিখছেন (শাশ্বতী, এনার)ধুন্দুলের লতা বা আকন্দের চারা যদিবা দেখেছি, তাও মনে হয় যেন বিগত জন্মের স্মৃতি, কাউরি গ্রাম-ফেরতা কোন গুনিনের সঙ্গেই কোনদিন কোন লেনাদেনা গড়ে ওঠেনি। না ভয়ের, না ভালবাসার। অবশ্য সে দেখলে শ্যাখের বিবি হালিমার ঘরকন্নাই বা কোন সুতোয় চেনা! তবু একুশ বছরের দিদির বিয়ের দায় মাথায় চাপানো চৌদ্দর ছোটভাই এর শিশু শ্রমের গল্পটা চেনা চেনা লাগে যে! আর তারই মাঝে লেখক কেমন বুনে দেন শবেবরাতের মোমের আলো আর দোলের চাঁদের পৃথগন্ন হওয়ার কিসসা। ... ...
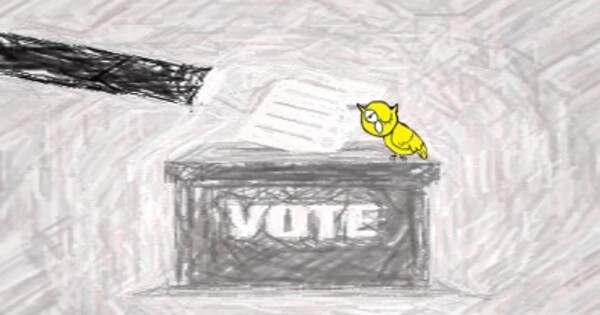
প্রযুক্তি নির্ভর নির্বাচন আসলে গণতন্ত্র হরণ নয় তো? - সুমন সেনগুপ্ত
বুলবুলভাজা | আলোচনা : রাজনীতি | ২৫ জানুয়ারি ২০২৩ | ৮১০ বার পঠিত | মন্তব্য : ৩, লিখছেন (হজবরল, সন্তোষ বন্দোপাধ্যায়, অনেক সমস্যা আছে - সমাধান চাই)ভারতের নাগরিকেরা কি তবে আর ভারতীয় গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ উৎসব, নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে চাইছেন না? অন্তত নির্বাচন কমিশনের তথ্য তো তাই বলছে। ২০১৯ সালের সাধারণ নির্বাচন এবং তারপরে যে কয়েকটি রাজ্যে নির্বাচন প্রতি ক্ষেত্রেই দেখা গেছে ভোটদানের হার ক্রমশ কমছে। গুজরাট বিধানসভা নির্বাচনের আগে, নির্বাচন কমিশন বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে মৌ চুক্তি অবধি করেছিল, যাতে সেই সব সংস্থাতে কর্মরত মানুষেরা ভোট দিতে অনীহা প্রকাশ না করেন। যে সমস্ত কর্মীরা নির্বাচনে অংশ নেবেন না, তাঁদের নামের একটি তালিকা অবধি প্রকাশ করার নির্দেশ দেওয়া হয়, নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে। বিরোধীদের তরফ থেকে অভিযোগ করা হয়, এই বন্দোবস্ত তো ‘বাধ্যতামূলক’ ভোটদানের প্রক্রিয়া, কোনও গণতন্ত্রে একজন মানুষ, নানান কারণে ভোট নাও দিতে চাইতে পারেন, তা’বলে কি একজন মানুষকে ভোটদানে অংশ নিতে বাধ্য করা যায়? ... ...

পূর্ব ইউরোপের ডায়েরি – কাজাখস্তান ৫ - হীরেন সিংহরায়
বুলবুলভাজা | ধারাবাহিক : ইতিহাস | ২৩ জানুয়ারি ২০২৩ | ১৪৬২ বার পঠিত | মন্তব্য : ৭, লিখছেন (হীরেন সিংহরায়, হীরেন সিংহরায়, Kishore Ghosal)আরতুরোস বললে, ‘দেখতে থাক। পাঁচ মিনিটের বেশি যদি লাগে, হোটেলে ফিরে গিয়ে আমার পয়সায় বিয়ার খাওয়াব। কৌতূহল বেড়ে গেল। বিয়ারের জন্য নয়। সপরিবারে পরায়া গাড়িতে কারো লিফট পাওয়া অসম্ভব মনে হচ্ছিল। তিরিশ বছর আগে জার্মানিতে হাত দেখিয়ে লিফট জোগাড় করার ভীষণ চল ছিল। নিজে করেছি। তবে সেটা অটোবানে। শহরে নয় -সেখানে সরকারি পরিবহন ব্যবস্থা আছে, আমেরিকার মতন নয়। কথ্য জার্মানে বলা হয়, বুড়ো আঙ্গুল (প্যার দাউমেন) দেখিয়ে সফর করা। নিরাপত্তা পরিস্থিতির অনিশ্চয়তার কারণে হয়তো জার্মানিতে এই যানযাত্রার পদ্ধতি প্রায় বিলীন এখন। ... ...

সীমানা - ২২ - শেখরনাথ মুখোপাধ্যায়
বুলবুলভাজা | ধারাবাহিক : উপন্যাস | ২৩ জানুয়ারি ২০২৩ | ২৩০৩ বার পঠিতআগুন জ্বললো পরের দিন, সম্পূর্ণ নতুন আবহে। এমনটা কাজি দেখেনি আগে; দোলের আগের দিন, সন্ধ্যে পেরিয়ে তখন রাত অনেকটাই। পরের দিন পূর্ণিমা, আজই আকাশ ভেসে যাচ্ছে আলোর বন্যায়। নানারকমের কাঠকুটো যোগাড় করে গ্রামের ছেলেরা এসে জমিদারবাবুর প্রাঙ্গনে আগুন জ্বালাল। ছেলের দল বলল নেড়াপোড়া, কিরণশঙ্কর বললেন চাঁচর। তারপর বললেন, ওদের নেড়াপোড়া কথাটাও কিন্তু বেশ যুক্তিযুক্ত। ধানকাটা হয়ে গেছে, পিঠেপায়েসের উৎসবও শেষ। এখন নতুন করে জমিতে কাজ শুরু হবে, তার আগে ক্ষেতে পড়ে-থাকা শস্যস্তম্ব, মানে, শস্য কেটে নেবার পর ক্ষেতে পড়ে থাকে যেটুকু, যাকে গ্রাম্য ভাষায় নেড়া বলে, তা পোড়ানো হবে। ... ...

নিশ্চিহ্ন হওয়ার মুখে জোশিমঠ - বনভূষণ নায়ক
বুলবুলভাজা | আলোচনা : পরিবেশ | ২১ জানুয়ারি ২০২৩ | ১১৫২ বার পঠিত | মন্তব্য : ৪, লিখছেন (দ, Parthapratim Nag, Subhro Bhattacharyya)
ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের গ্যারান্টি: কী এবং কীভাবে? - যোগেন্দ্র যাদব
বুলবুলভাজা | আলোচনা : রাজনীতি | ২০ জানুয়ারি ২০২৩ | ৯০৪ বার পঠিত | মন্তব্য : ১, লিখছেন (মোহাম্মদ কাজী মামুন)সমস্যা শুধু এবছরের বা মধ্যপ্রদেশের নয়। এই পর্যন্ত ভারত জোড়ো যাত্রায় আমি ৭টি রাজ্যের কৃষকদের সঙ্গে আলোচনা করার সুযোগ পেয়েছি। একেক জায়গার সমস্যা একেক রকম। কিন্তু একটি যন্ত্রণা দেশের প্রত্যেক কৃষককে এক করে দেয়: বাজারে ফসলের সঠিক দাম পাওয়া যায় না। পেঁয়াজ এবং রসুনের মত শাকসবজি বা ফলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য নেই, তবে যে সব ফসলের সহায়ক মূল্য ঘোষণা করা হয়েছে তাও পাওয়া যায় না। মুগ, ছোলা, অড়হরের মত ডালের জন্য কাগজে ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ঘোষণা করা হয় কিন্তু বিক্রি হয় না। ফলে বাজারে ঘোষিত ন্যূনতম মূল্য থেকে এক হাজার বা দুই হাজার টাকা ক্ষতি হয় কৃষকের। ধান ও গমের সরকারি ক্রয় সত্ত্বেও অধিকাংশ জায়গায় কৃষক লোকসানের মুখে পড়ে ব্যবসায়ীর কাছে ফসল বিক্রি করেন। ... ...

এক কাপ চা - পর্ব ৩ - কল্যানী ঘোষ
বুলবুলভাজা | আলোচনা : শিক্ষা | ২০ জানুয়ারি ২০২৩ | ৮০৩ বার পঠিত | মন্তব্য : ৩, লিখছেন (kk, Esha Kar, Sima Ghosh)না, যা ভাবছেন ঠিক তা নয়, এটা দার্জিলিং বা মসালা চা নয়। এই "এক কাপ চা" লেখাটা ক্যালিফোর্নিয়ার, স্যান ডিয়েগোর একটি হাই স্কুলে বিশেষ ভাবে সক্ষম (স্পেশাল এডুকেশন) নবম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীদের যৌন শিক্ষার ক্লাসের বোর্ডে জ্বলজ্বল করছে। এখানে হাইস্কুলে ঢুকেই যৌন শিক্ষা বাধ্যতামূলক। অন্য ছাত্রছাত্রীদের এ বিষয়ে শিক্ষাদান অনেকটাই সহজ, কিন্তু এদের? যারা অটিস্টিক, বা ADHD (মনোযোগ ঘাটতি) কিম্বা ডাউন সিনড্রোম এ আক্রান্ত, অথবা প্রায় অন্ধ ও বধির তাদের কী করে এই রকম একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া যাবে? অথচ দিতেই হবে, কারণ যৌন নিগ্রহের আশঙ্কা এদেরই সব থেকে বেশি, কয়েকজন তো শিশুকালেই তাদের সৎ বাবা অথবা মায়ের পুরুষ বন্ধুর দ্বারা অত্যাচারিত হয়ে মানসিক ভারসাম্য প্রায় হারাতেই বসেছে। ... ...
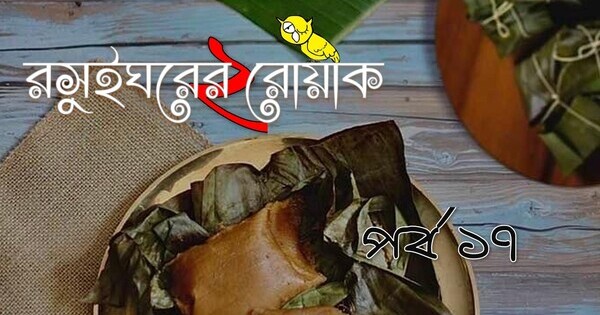
রসুইঘরের রোয়াক (দ্বিতীয় ভাগ) - ১৭ - স্মৃতি ভদ্র
বুলবুলভাজা | খ্যাঁটন : খানা জানা-অজানা | ১৯ জানুয়ারি ২০২৩ | ১৩৫৮ বার পঠিত | মন্তব্য : ২, লিখছেন (জয়, দ)আজ আকাশের গায়ে অন্ধকার একটুও বসতে পারছে না। সুপারি বাগানের মাথায় বসে থাকা চাঁদটা এরইমধ্যে আরোও বড় হয়ে উঠেছে। সেই চাঁদের আলো সন্ধ্যা আকাশের গা থেকে ঠিকড়ে পড়ছে আমাদের উঠোনে। উঠোনে এবার পাঁচ প্রদীপ জ্বলে উঠল। কলার মাইজে একমুঠো ধান, একগোছা দূর্বা আর ক’খানা কড়ি রাখল ঠাকুমা। আর কলার খোলে পড়ল তালের ক্ষীর, তালের ফুলুরি, তিলের ক্ষিরশা আর পাতাপোড়া পিঠা। ... ...
- পাতা : ২৪১২৪০২৩৯২৩৮২৩৭২৩৬২৩৫২৩৪২৩৩২৩২
-
গুরুচণ্ডা৯-র গ্রাহক হোন
কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে গুরুচণ্ডা৯-র গ্রাহক হোন। গুরুচণ্ডা৯তে প্রকাশিত লেখাগুলি পেতে চাইলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যুক্ত হোন, অথবা, আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলটির গ্রাহক হোন।
- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই
- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... সমরেশ মুখার্জী, kk, রমিত চট্টোপাধ্যায়)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... )
(লিখছেন... b)
(লিখছেন... )
- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন
(লিখছেন... )
(লিখছেন... )
(লিখছেন... অরিন, সমরেশ মুখার্জী, Arindam Basu)
(লিখছেন... হীরেন সিংহরায়, হীরেন সিংহরায়, Debabrata Mandal )
(লিখছেন... Tanusree Mukherjee )
- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... lcm, পাঠক, সুকি)
(লিখছেন... এঃ, সত্যেন্দু সান্যাল, সুদীপ্ত)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... Arindam Basu, Arindam Basu, Arindam Basu)
(লিখছেন... Arindam Basu, Kunal Chattopadhyay, Arindam Basu)
- কি, কেন, ইত্যাদি
- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...
- আমাদের কথা
- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...
- বুলবুলভাজা
- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...
- হরিদাস পালেরা
- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...
- টইপত্তর
- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...
- ভাটিয়া৯
- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...
- বুলবুলভাজা গুরুচন্ডা৯-র সম্পাদিত বিভাগ। এই বিভাগে প্রকাশিত লেখা অন্যত্র প্রকাশের ক্ষেত্রে গুরুচণ্ডা৯ ও লেখকের অনুমতি ও উল্লেখ প্রয়োজনীয় । টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই । ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত ।




