-
বুলবুলভাজা
-
এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়।
বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচণ্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। - গুরুভার আমার গুরু গুরুতে নতুন? বন্ধুদের জানান
- সময়ানুক্রমে | সদ্য আলোচিত | মন্তব্য অনুসারে | পঠিত অনুসারে | লেখক তালিকা
-
- নতুন আলোচনা
-
বিষয়ের শিরোনাম*:বিষয়বস্তু*:
- পাতা : ২৬৭২৬৬২৬৫২৬৪২৬৩২৬২২৬১২৬০২৫৯২৫৮

মহারাজ ছনেন্দ্রনাথ আর বিরাট রাজার মাঠ - রমিত চট্টোপাধ্যায়
বুলবুলভাজা | ধারাবাহিক : গপ্পো | ২৭ জুলাই ২০২৪ | ১৭৭ বার পঠিত | মন্তব্য : ৪, লিখছেন (রমিত চট্টোপাধ্যায়, ., রমিত চট্টোপাধ্যায়)বড়দা তখন আর কথা বলবে কি, চোখের সামনে যেন দেখতে পাচ্ছে মাঠটা পুরো গমগম করছে, ভাঙা বাড়িটাও গোটা হয়ে গিয়ে ঝকঝকে তকতকে, লোকে লোকে জায়গাটা ছয়লাপ। মাঠ জুড়ে বড় বড় টেবিল পাতা, পাশে সার দিয়ে চেয়ার। ওয়েটাররা রান্নাঘর থেকে প্লেটে করে সব গরমাগরম খাবার দাবার এনে টেবিলে রেখে যাচ্ছে। বড় ঘরটা জুড়েও সব বড় বড় শ্বেত পাথরের টেবিল রাখা। সেখানেও লোক ভর্তি। ওয়েটাররা এদিক সেদিক ছোটাছুটি করছে। রান্নাঘরে বিশাল বিশাল হাঁড়ি, ডেকচি, কড়া নিয়ে ঠাকুররা সব রান্না করছে। বাড়িটার সামনে জ্বল জ্বল করছে নাম- 'শিয়ালদা রেস্টুরেন্ট'। বড় ঘরের এক কোণায় সাদা গদি পাতা। তাতে বালিশে হেলান দিয়ে আয়েশ করে বাবা বসে আছেন। পাশের টেবিলে ক্যাশ বাক্স সামলিয়ে হিসেব দেখছে জগন্নাথদা। ওয়েটাররা এসে মুখস্ত হিসেব বলছে আর সেই অনুযায়ী লিখে নিচ্ছে পরপর। ঠিক যেন কালকের ঘটনা। ... ...

বিপ্লবের আগুন - পর্ব পনের - কিশোর ঘোষাল
বুলবুলভাজা | ধারাবাহিক : উপন্যাস | ২৭ জুলাই ২০২৪ | ৪৯ বার পঠিত | মন্তব্য : ২, লিখছেন (অসিতবরণ বিশ্বাস , দ)“হ্যাঁ, রাজনীতি ব্যাপারটা আদতে খচ্চরদেরই সৃষ্টি। ভালো আর মন্দ, ঔদার্য আর তঞ্চকতা, সহমর্মীতা আর নিষ্ঠুরতাকে মনের মধ্যে পাশাপাশি বসিয়ে রাজনীতির চর্চা করতে হয়। কবিরাজবুড়োর জন্যে আমি বাইরে শুধু লোক-দেখানে কাঁদব - তা নয়, মনে মনে সত্যিই কষ্ট পাবো। তাঁর বিচক্ষণতার জন্যে রাষ্ট্রের অভিনব এই পরিকল্পনাটাই হয়তো ভেস্তে যাবে। অতএব মরতে তাঁকে হবেই। কিন্তু সে মৃত্যুতে বোধহয় আমিই সব থেকে বেশি আঘাত পাবো। তবে মনে মনে একথা চিন্তা করে সান্ত্বনা পাব যে, উনি নিজের জীবন দিয়ে আমার কাজটাকেই অনেক সহজ করে দিয়ে গেলেন"। ... ...

কাদামাটির হাফলাইফ - ইট পাথরের জীবন - ইমানুল হক
বুলবুলভাজা | ধারাবাহিক : স্মৃতিকথা | ২৭ জুলাই ২০২৪ | ৫৭ বার পঠিত | মন্তব্য : ২, লিখছেন (PRABIRJIT SARKAR, অমিতাভ চক্রবর্ত্তী)স্বাধীন দেশে রাজা এবং প্রজার ধারণা এক মানসিক দাসত্ববৃত্তি থেকে আসে। তাই সাধারণতন্ত্র না বলে প্রজাতন্ত্র দিবস বলেন কেউ কেউ। । আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে খুব ঘটা করে পালন হতো ২৬ জানুয়ারি ও ১৫ আগস্ট। প্রধানশিক্ষক ছিলেন আমার বড়োমামা। কংগ্রেসের বড়ো নেতা। বোঁদে দেওয়া হতো। পতাকা তোলার পর গোটা গ্রাম মিছিল করে ঘোরা শেষে। মাঝপথে কেউ যাতে না পালায়, তাই শেষে মিষ্টি। আমরা সিপিএম বাড়ির ছেলে। পিছনের দিকে থাকতাম। বন্দে বলে আওয়াজ উঠলেই আলতো করে বলে উঠতো কেউ কেউ, বোঁদে ছাগলের পোঁদে। তবে বোঁদে খাওয়ার সময় এ-সব কারও মনে থাকতো না। আমার মনে পড়ে না জুনিয়র হাইস্কুলে এ-সব পতাকা উত্তোলনের রেওয়াজ ছিল কি না! তবে সেহারা স্কুলে পড়ার সময় বেশ ভিড় হতো। ছাদে। বক্তৃতাও হতো। মিল মালিকের ছেলে কংগ্রেসের অবদান বললে, তেড়ে আধঘন্টা বক্তৃতা করে ধুইয়ে দিয়ে বলেছিলাম, ইয়ে আজাদি আধা হ্যায়। টাটা বিড়লা গোয়েঙ্কারা দেশ লুঠছে। তখন তো আদানি আম্বানিদের দেখি নি। তাহলে কী বলতাম জানি না। তখন বলেছিলাম, মাথাপিছু ৬০০ টাকা ঋণ। ... ...

ক্যালিডোস্কোপে দেখা – ভো-কাট্টা - অমিতাভ চক্রবর্ত্তী
বুলবুলভাজা | ধারাবাহিক : স্মৃতিকথা | ২০ জুলাই ২০২৪ | ৪৬৯ বার পঠিত | মন্তব্য : ২৩, লিখছেন (অভিজিৎ। , অমিতাভ চক্রবর্ত্তী, অভিজিৎ। )বাবা বারান্দায় বসে একধাপ নিচের সিঁড়িটায় একটা যুৎসই উচ্চতার কাঠের টুকরো রেখে তার উপর বাঁশের টুকরোটা দাঁড় করিয়ে দা দিয়ে সেটাকে লম্বালম্বি কয়েকটা টুকরোয় চিরে ফেলল। তারপর তাদের একটার গা থেকে দা দিয়ে কয়েকটা ছিলকা বার করে নিয়ে ছুরি দিয়ে সেগুলোকে চেঁছে চেঁছে কয়েকটা মসৃণ এবং নমনীয় কাঠি বানিয়ে নিল। এরপর রঙিন কাগজের বান্ডিল থেকে একটা কাগজকে টেনে নিয়ে সেটাকে ভাঁজ করে, ভাঁজ বরাবর ছুরি টেনে তার থেকে একটা বর্গাকার টুকরো বার করে আনল। এরপর ঐ কাঠিগুলোর একটাকে সেই কাগজের টুকরোটার উপর রেখে কাঠির গোড়া যদি এক নম্বর কোণায় রাখা হয়েছে ধরি, তবে অন্য প্রান্তকে তিন নম্বর কোণার দিক করে বসিয়ে কোণা ছাড়িয়ে দুই কি তিন ইঞ্চি দূরে ছুরি দিয়ে কাঠির গায়ে দাগ কেটে তারপর দাগ বরাবর দু’ টুকরো করে, দাগের প্রান্ত আর গোড়ার প্রান্তকে একটা সুতো দিয়ে আলগা করে বেঁধে একটা ধনুক বানিয়ে ফেলল। সুতোটা তখনো ঢিলা রেখে ধনুকটাকে এবার চৌকো কাগজের উপর বসিয়ে ঠিকমত আকারে এনে সুতোর সেই ছিলা টাইট করে বেঁধে ফেলা হল। ধনুকের দুই মাথা কাগজের এক আর তিন নম্বর কোণা ছুঁয়ে আছে। আমরা ভিতরে ভিতরে উত্তেজনায় ছটফট করলেও শান্তভাবে বসে দেখে যাচ্ছি। ... ...

বৈদিক গণিত বিপন্ন? - সুনন্দ পাত্র
বুলবুলভাজা | আলোচনা : উচ্চশিক্ষার আনাচকানাচ | ২৩ জুলাই ২০২৪ | ২৪৪২ বার পঠিত | মন্তব্য : ৩৮, লিখছেন (কচ্ছপ, Debasis Bhattacharya, Debasis Bhattacharya)গত ১২ই জুলাই, শুক্রবার, অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে পনেরোতম আন্তর্জাতিক গণিত-শিক্ষণ কংগ্রেস-এর সম্মেলন থেকে অধ্যাপক জয়শ্রী সুব্রহ্মনিয়নকে নিরাপত্তা-আধিকারিকরা প্রহরা দিয়ে বের করে দেন। তাঁর ব্যাজ বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং রেজিস্ট্রেশন প্রত্যাহার করা হয়। কারণ হিসেবে তাঁকে বলা হয়, যে, সেদিন সকাল ন-টায় অধ্যাপক আশিস অরোরা-র বৈদিক গণিতের অধিবেশনে তাঁর করা কিছু মন্তব্যকে কিছু অন্য অংশগ্রহণকারীর শাসানিমূলক ও ভীতিপ্রদ মনে হয়েছে। কতটা আতঙ্কের উদ্রেককারিণী এই ভারতীয় গণিত-অধ্যাপক? কতটা ভয়ঙ্কর তাঁর উপস্থিতি, যার ফলে তাঁকে শিক্ষকদের সম্মেলন থেকে বের করে দিতে হয়? ‘বৈদিক গণিত’ ঠিক কীরকম বিপন্ন হয়েছিল তাঁর উপস্থিতিতে? এসব কথা জানতে, সেই অধিবেশনেরই আরেক শ্রোতা এবং ওই সম্মেলনের আরেক নিমন্ত্রিত বক্তা, ওহায়ো স্টেট ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক থিওডর চাও-এর বয়ান পড়ে ফেলুন। ... ...

এই বর্ষার কবিতা - সোমনাথ রায়
বুলবুলভাজা | কাব্য | ২৬ জুলাই ২০২৪ | ১৪৬ বার পঠিত | মন্তব্য : ১, লিখছেন (অমিতাভ চক্রবর্ত্তী)সে-কবিতা কেন লিখে যাচ্ছি আজও এতদিন ধরে তাই ভাবি অনর্থক কেন আহ্বান করছি ধারাপাত শব্দ এযাবৎ অথচ অবাক আমি বুঝিইনি আকাশের দাবি সে-বিকেলে রাস্তার আলস্যে ছাউনির নিচে অপেক্ষা করেছে সাইকেল ... ...

তুমি তো প্রহর গোনো, তারা মুদ্রা গোনে কোটি কোটি - অতনু চক্রবর্তী
বুলবুলভাজা | আলোচনা : রাজনীতি | ২৭ জুলাই ২০২২ | ১২০৩৪ বার পঠিত | মন্তব্য : ২৫৫, লিখছেন ( দীপ, দীপ, দীপ)
সিজনস অব বিট্রেয়াল – নবম পর্ব - দময়ন্তী
বুলবুলভাজা | ধারাবাহিক | ০৬ অক্টোবর ২০১৮ | ১৯৫৩♦ বার পঠিত | মন্তব্য : ২০, লিখছেন (Aditi Dasgupta, দ, r2h)জামুকে দেখলে টুনুর মনে হয় ইতিহাস বইয়ের খানিক টুকরো যেন হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে। কতরকম অজানা সব গল্প যে বলে। সরলা নেমে দেখেন ছেলে বেশ পরিস্কার শার্ট প্যান্ট পরে ভব্যিযুক্ত হয়ে এসেছে। খাবার বেড়ে সামনে বসে কথা বলতে বলতে খেয়াল করলেন এও আজ একটু অন্যমনস্ক। হুঁ, হাঞ্জি আর ঘাড় নেড়েই কাজ চালাচ্ছে। ওর হিন্দিবাংলা মেশানো তড়বড়ে কথা আজ নেই। খেয়ে হাত মুখ ধুয়ে, থালা গেলাস মেজে ধুয়ে রেখে কিছু কাজ আছে কিনা জিগ্যেস করে তারপর ইতস্তত ভাবে জানায় ওর একটা আর্জি আছে মা’জির কাছে। ঢোলা শার্টের পকেটে হাত গলিয়ে তুলে আনে একটা কাগজে মোড়া পাতলা কি যেন। ঐ জিনিষটা সে সরলার কাছে রেখে যেতে চায়, ওর থাকার কোন ঠিক নেই, এটা আরেকজনের জিম্মা করা জিনিষ, চুরি হয়ে গেলে উপরওলার কাছে অপরাধী হয়ে যাবে জামু। সরলা বলেন যার জিনিষ তাকেই দিয়ে দিলে তো হয়। জামু নাকি জানেই না সে মানুষ কোথায়। আবার ওর মুখ থমথমে হয়ে যায়, চোখদুটো কেমন অচেনা। ... ...

ক্যালিডোস্কোপে দেখি - মন বসানো - অমিতাভ চক্রবর্ত্তী
বুলবুলভাজা | ধারাবাহিক : স্মৃতিকথা | ১৮ মে ২০২৪ | ৮২৯ বার পঠিত | মন্তব্য : ১৯, লিখছেন (অমিতাভ চক্রবর্ত্তী, Aditi Dasgupta, অমিতাভ চক্রবর্ত্তী)উত্তরবঙ্গে কয়েকটি সপ্তাহ কাটিয়ে বুঝে গেলাম এইবারে এক সম্পূর্ণ আলাদা দুনিয়ায় এসে হাজির হয়েছি। এবং এখান থেকে আর আগের জগতে ফিরে যাওয়ার কথা বড়োরা কেউ ভাবছে না। মন বসাতে সময় লেগেছিল। তারপর একটু একটু করে সেই নতুন জগৎ আমায় ঘিরে নিল। ... টান এক মজার অনুভূতি। যে তিন বছর উত্তরবঙ্গে ছিলাম, যখন তখন ভাবতাম কবে আমাদের দমদম ক্যান্টনমেন্টের ভাড়াবাড়ির ঘরে ফিরব। আর উত্তরবঙ্গ ছেড়ে আসার কয়েকবছর পর থেকে কি যে এক চোরাটান ছেয়ে থেকে অস্তিত্ব জুড়ে – সেই তোর্সাতীর-এর জন্য! ... ...

বিপ্লবের আগুন - পর্ব চোদ্দ - কিশোর ঘোষাল
বুলবুলভাজা | ধারাবাহিক : উপন্যাস | ২০ জুলাই ২০২৪ | ২৯৭ বার পঠিত | মন্তব্য : ৪, লিখছেন (অমিতাভ চক্রবর্ত্তী, মোহাম্মদ কাজী মামুন , Kishore Ghosal)... যে কথা বলছিলাম, রাজধানীর ঘটনাটা যেদিন ঘটেছিল, শুনেছি সেই রাত্রেই ভল্লা রাজধানী থেকে রওনা হয়েছিল। রাজধানী ছাড়ার পর চতুর্থ দিন ভোরে সে আমাদের গ্রামে এসে পৌঁছেছিল পায়ে হেঁটে। বিপর্যস্ত অবস্থায়। রাজধানী থেকে আমাদের গ্রামের যা দুরত্ব, সেটা তিনদিন, তিন রাত পায়ে হেঁটে আসা অসম্ভব। বিশেষ করে ওরকম অসুস্থ অবস্থায়। তার মানে দাঁড়াচ্ছে ও বেশিরভাগ পথটাই এসেছিল হয় ঘোড়ায় চড়ে অথবা রণপায়.. ... ...
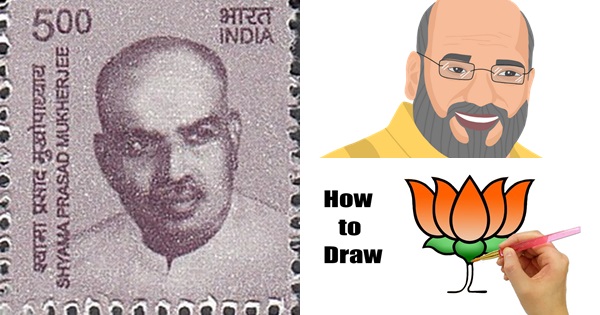
শ্যামাপ্রসাদ: সত্য ঘটনা অবলম্বনে - অভিরূপ গুপ্ত
বুলবুলভাজা | আলোচনা : রাজনীতি | ০৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১ | ২৭৩৫২ বার পঠিত | মন্তব্য : ২২৩, লিখছেন (Ramit Chatterjee, Unanonimous Yelok, Basic)সরকারি ত্রাণব্যবস্থা যখন হিমশিম খাচ্ছে, তখন বেসরকারি ত্রাণ শুরু হল শ্যামাপ্রসাদের পরিচালনায়। তিনি 'বেঙ্গল রিলিফ কমিটি' বা বিআরসির রিলিফ কমিশনার নিযুক্ত হলেন এবং এই দুর্ভিক্ষের হাহাকারের মধ্যেও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করার সুযোগ ছাড়লেন না। ত্রাণকেন্দ্র স্থাপন করলেন কেবলমাত্র সেই সব গ্রাম এবং ওয়ার্ডে যেখানে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। বিআরসির সঙ্গে সঙ্গে শ্যামাপ্রসাদের তত্ত্বাবধানেই তৈরি হল হিন্দু মহাসভা রিলিফ কমিটি। ... ...

মহারাজ ছনেন্দ্রনাথ, খেলনাবাড়ি আর পক্ষীরাজ ঘোড়ার গল্প - রমিত চট্টোপাধ্যায়
বুলবুলভাজা | ধারাবাহিক : গপ্পো | ১৩ জুলাই ২০২৪ | ৫৩০ বার পঠিত | মন্তব্য : ২৩, লিখছেন (রমিত চট্টোপাধ্যায়, &/, রমিত চট্টোপাধ্যায়)ছেনু দেখল, সত্যিই তো, পকাইকে তো এবার চড়তে দিতেই হয়, বেচারি এতক্ষণ ধরে অপেক্ষায় রয়েছে। তার ওপর ওরই ঘোড়া যখন। আজ সকালে পকাইদের বাড়ি এই ঘোড়াখানা আসতেই পকাই তাড়াতাড়ি ছেনুকে ডেকে এনেছে। সেই ঘোড়াখানা দেখেই তো ছেনু আনন্দে আত্মহারা। উফ্, ঘোড়া বটে একখানা। কি সুন্দর লালের ওপর সাদা,কালো, হলুদ দিয়ে রং করা, পিঠের উপর চওড়া করে বসার আসন পাতা, ঘাড়ের কাছে কেশরের পাশ দিয়ে আবার ধরার জন্য দুটো হাতল রয়েছে, খাড়া খাড়া কান, সাথে তেমনি টানা টানা চোখ - দেখেই চোখ জুড়িয়ে চায়। এ যা ঘোড়া, পক্ষীরাজ না হয়ে যায় না! সত্যিই, মহারাজ যেন এমন একটা ঘোড়ারই সন্ধানে ছিলেন এতদিন ধরে। তাই সে ঘোড়া দেখে আর লোভ সামলাতে পারেননি, পকাইয়ের জন্য আনা ঘোড়ায় নিজেই টপ করে বসে পড়েছেন। আর ঘোড়ায় চেপে টগবগ টগবগ করে সেই যে ছুটিয়েছেন, ডানা মেলে এদিক ওদিক ঘোরার মধ্যে আর সময়ের হুঁশ ছিল না। পকাই ধৈর্য হারিয়ে আবার ঘরে চলে গিয়েছিল, ফিরে এসেও যখন দেখল মহারাজের ঘোড়ায় চড়া শেষ হয়নি, তখন চিৎকার জুড়তেই ছেনুর টনক নড়ল। ... ...

কাদামাটির হাফলাইফ - ইট পাথরের জীবন - ইমানুল হক
বুলবুলভাজা | ধারাবাহিক : স্মৃতিকথা | ২০ জুলাই ২০২৪ | ২৬২ বার পঠিত | মন্তব্য : ২, লিখছেন (অমিতাভ চক্রবর্ত্তী, Eman Bhasha)বড়ো শখ করে এক দহলিজ/ কাছারি/ খানকা/ বৈঠকখানা বানিয়েছিলেন হেকিম সাহেব। সেটা আমিও দেখতে পেয়েছি। খড়ের বদল পাট দিয়ে পাঠ। দেওয়াল শোনা কথা, ডিমের লালা দিয়ে পালিশ করা। বেতের চাল। তারপরে খড়। আর দামি কাঠের হরেক কাছ। প্রতিটা খুঁটি বরগায় কাজ। লোকে দেখতো আসতো, এই শখের কাজ। দরজাও সেকালের মতো কারুকার্যময়। ঝাড়বাতি ঝুলতো। পাঙ্খাটানার ব্যবস্থাও ছিল। দহলিজের দখিন দিকে নিমগাছ। নিমের হাওয়া খাবেন, তাই। ... ...

ক্যালিডোস্কোপে দেখি - দূরবীন - অমিতাভ চক্রবর্ত্তী
বুলবুলভাজা | ধারাবাহিক : স্মৃতিকথা | ০৬ এপ্রিল ২০২৪ | ৫৫৬ বার পঠিত | মন্তব্য : ১০, লিখছেন (সমরেশ মুখার্জী, অমিতাভ চক্রবর্ত্তী, Aditi Dasgupta)অনেক দূরের জিনিষ দেখতে পাওয়া আর তার ফলে যে সব তথ্য যোগাড় হল তাই দিয়ে অতীতের বিভিন্ন সম্ভাব্য ছবি ফুটিয়ে তোলা, আধুনিক মহাকাশ গবেষণা আর জ্যোতির্বিজ্ঞানের এক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কত রকমের তরঙ্গের ব্যবহার, কত রকমের দূরবীন, কত মাপজোক। অনেকে নিজের দরকারে বা শখে একনলা কি দোনলা দূরবীন কেনেন, ব্যবহার করেন, সাজিয়ে রাখেন। আমি এ পর্যন্ত যে দু-তিনটি কিনেছি, নিতান্ত মামুলি, খেলনার বেশি মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য নয়। হারিয়েও গেছে তারা। তবে অন্য একটি দূরবীন মাঝে মাঝে ব্যবহার করি। স্মৃতির দূরবীন, ফেলে আসা জীবনের ছবি দেখতে। কতটা অতীত দেখতে পাওয়া যায়? যাচ্ছে? বেশীর ভাগ ছবি-ই ফোকাসের বাইরে। তবু শব্দের পর শব্দ সাজিয়ে, যেন ডিজিটাইজ করে, পিক্সেল জুড়ে জুড়ে রেন্ডারিং করে নানা ভাঙ্গাচোরা টুকরো থেকে এক একটা ছবি বার করে আনা। যা ঘটেছিল তার কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়া, যতটা পারা গেল। ... ...

ওরা বীর, ওরা আকাশে জাগাত ঝড় - ঊনিশ শতক – চিকিৎসক-নারী কাদম্বিনী গাঙ্গুলি - জয়ন্ত ভট্টাচার্য
বুলবুলভাজা | আলোচনা : সমাজ | ১১ জানুয়ারি ২০২১ | ৬৯৬১ বার পঠিত | মন্তব্য : ৫০, লিখছেন (Sumit chakraborty , Sumit chakraborty , সুভাষ রাহা।)কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে মহিলা ছাত্রদের ভর্তি করা নিয়ে চিন্তাভাবনা ১৮৭৬ সাল থেকে শুরু হয়। সেসময়ের বাংলার লেফটন্যান্ট গভর্নর স্যার রিচার্ড টেম্পল এ বিষয়ে উৎসাহী ছিলেন। ১৮৮১-তে প্রধানত ভর্তি হতে উৎসাহী ছাত্রীদের অভিভাবকদের চাপে এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট মেডিক্যাল কলেজের কর্তৃপক্ষকে চিঠি দেয় “discussing the question of accepting an inferior admission qualification for lady students.” (Centenary Volume, 1935, p.46) এই দলিলের ভাষ্য অনুযায়ী সম্ভবত ১৮৮৪ সালে প্রথম মহিলা হিসেবে কাদম্বিনী গাঙ্গুলি অ্যাডমিশন নেন (বা বলা ভালো অ্যাডমিশনের অধিকার পান)। উল্লেখ করা দরকার যেহেতু অক্সফোর্ড এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে মহিলাদের প্রবেশাধিকার ছিলনা সেজন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ মহিলাদের ভর্তির ব্যাপারে গররাজি ছিল। ... ...

বিশ্বাসঘাতকতার আখ্যান 'সিজনস অব বিট্রেয়াল' - অরিজিৎ গুহ
বুলবুলভাজা | পড়াবই : প্রথম পাঠ | ১৩ নভেম্বর ২০১৯ | ১৭২৪♦ বার পঠিত | মন্তব্য : ৫, লিখছেন (দ, রমেন, রমিত চট্টোপাধ্যায়)১৯৪৭ আর্থ' এ একটা দৃশ্য ছিল অমৃতসর থেকে লাহোরের দিকে আসা উদ্বাস্তু পরিপূর্ণ একটা ট্রেন লাহোর স্টেশনে এসে যখন দাঁড়িয়েছিল, লাহোরের আত্মীয়স্বজনরা ট্রেনের ভেতর থেকে কেউ বেরোচ্ছে না দেখে যখন উঁকি মেরে দেখতে যায়, এক ঝলক দেখেই আতঙ্কে বাইরে ছিটকে সরে আসে, কেউ কেউ বা ওখানেই বমি করে দেয়। ট্রেনটা ভর্তি ছিল শুধু ছিন্নভিন্ন লাশে। একজনও কেউ জীবিত ছিল না ট্রেনে। লাহোর থেকে যখন অমৃতসরে ট্রেন যায় এদিকের উদ্বাস্তুদের নিয়ে, তখন সেই ট্রেনটাও পালটা লাশে ভরে ওঠে। অমৃতসর স্টেশনের আত্মীয় স্বজনরাও ঠিক একইভাবে আতঙ্কে সিঁটিয়ে উঠেছিল। সিনেমায় ওই দৃশ্যটা দেখে মনে মনে ভয় পেয়েছিলাম। পরে ভেবেছিলাম সিনেমার প্রয়োজনে অনেক কিছুই তো দেখাতে হয়, তাই এটাও হয়ত বানানো। এরকম যে বাস্তবে হতে পারে কখনো মাথাতেও আসে নি। অনেক অনেক পরে মান্টো পড়ার সময় বুঝেছিলাম এরকম কেন, এর থেকেও অনেক সাঙ্ঘাতিক জিনিস মানুষ করতে পারে। উন্মাদনার চরম সীমায় মানুষ যে কী করতে পারে আর কী করতে পারে না, তা মানুষ নিজেও জানে না। গুরুচণ্ডালী পাবলিকেশনের 'দময়ন্তী'র লেখা 'সিজনস অব বিট্রেয়াল' আবার সেই উন্মাদনার দিনগুলোতে নিয়ে ফেলছিল যেন। ... ...

চেকিয়া এক - হীরেন সিংহরায়
বুলবুলভাজা | ধারাবাহিক : ইতিহাস | ২০ জুলাই ২০২৪ | ৪০০ বার পঠিত | মন্তব্য : ৭, লিখছেন (হীরেন সিংহরায়, Rouhin Banerjee, R.K)আলাপ জমে গেলো ফ্রান্তিসেকের সঙ্গে। টি টুয়েন্টি নামক দানবের দুরাচার শুরু হবার আগে টেস্ট ক্রিকেটের মাঠে গল্প বেশি জমতো - অনেকক্ষণ যাবত মাঠে কিছুই ঘটে না, স্যাকরার ঠুক ঠাক চলে ব্যাটে বলে। ফুটবলের মাঠে সেটা সম্ভব নয়। তবু খেলার আগে, মাঝে, হাফ টাইমে কিছু কথা। আমরা তাঁকে একাধিক বিয়ারে আপ্যায়িত করেছি, কিছুতেই দাম দিতে দেব না! ভারত ও পূর্ব ইউরোপের ভাইচারা যুগ যুগ স্থায়ী হোক। দুজন ভারতীয়ের সঙ্গে এই ফ্রাঙ্কফুর্টের মাঠে দেখা হবে তিনি ভাবতে পারেন নি! আমার ট্রিভিয়া লাইব্রেরির শ্রীবৃদ্ধির জন্য যত না প্রশ্ন, ভারত সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞানস্পৃহা অনেক বেশি। ততক্ষণে তাঁর টিম আইনত্রাখত ফ্রাঙ্কফুর্টের হাতে বেশ ঝাড় খাচ্ছে, ৩-০ গোলে পিছিয়ে এবং তাঁর মনোযোগ বিভ্রান্ত। তাই প্রস্তাব দিলাম- তিনি যদি চান আমরা একত্র হেঁটে শহরে ফিরতে পারি, এক ঘণ্টার পথ। ট্রামে বেজায় ভিড় হবে। ফ্রান্তিসেক বললেন যদি আমরা তাঁকে ট্রেন স্টেশনের কাছাকাছি অবধি সঙ্গ দিতে পারি তাঁর খুব উপকার হয়, রাতের ট্রেন ধরবেন। সেটাই আমাদের লজিস্টিক, ফ্রাঙ্কফুর্ট হাউপটবানহফের সামনে আমরা বারো নম্বর ট্রাম ধরে বাড়ি ফিরব। ... ...

মহারাজ ছনেন্দ্রনাথ ও বিদেশি চকলেটের বাক্স - রমিত চট্টোপাধ্যায়
বুলবুলভাজা | ধারাবাহিক : গপ্পো | ১৫ জুন ২০২৪ | ৮৯১ বার পঠিত | মন্তব্য : ১৮, লিখছেন (রমিত চট্টোপাধ্যায়, Aditi Dasgupta, রমিত চট্টোপাধ্যায়)আজকে সকালে তেতলার পিসিমার কাছে যে চিঠিটা এল, দাদা মানে পিসিমার ছেলে অনেকক্ষণ ধরে পিসিমাকে পড়ে পড়ে শোনাচ্ছে। ছেনু গিয়ে দু'বার দরজার সামনে থেকে ঘুরেও এল, কত লম্বা চিঠি রে বাবা! শেষে আর থাকতে না পেরে ছেনু গিয়ে পিসিমাকে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করেই ফেলল, কার চিঠি গো? দেখা গেল অদ্ভুত ব্যাপার, পিসিমা হাসছে, অথচ চোখের কোণে জল, পিসিমা হেসে বলল, কে আসছে জানিস? কান্টু আসছে রে কান্টু, তোর কান্টু দাদা। এদ্দিন পর ও আসছে, শুনে বিশ্বাসই করতে পারছি না, তাই তো বারবার করে শুনছি। ছেনু ছোট্ট থেকে পিসিমার কাছে কান্টুদার অনেক গল্প শুনেছে, কিন্তু কোনোদিন কান্টুদাকে চোখে দেখেনি আজ পর্যন্ত। অবশ্য দেখবেই বা কি করে, ছেনুর জন্মের আগেই তো পিসিমার বড় ছেলে কান্টুদা সেই সাত সমুদ্দুর তেরো নদী পার করে কি একটা দেশ আছে, কানাডা না কি নাম, সেইখানে চলে গিয়েছিল। সেই থেকে সেখানেই থাকে আর মাঝে মধ্যে চিঠি লিখে খবরাখবর জানায়। শুরুর দিকে বাংলায় লিখত বটে কিন্তু পরে কি জানি কেন শুধু ইংরেজিতেই চিঠি পাঠায়, তাই অন্যরা পিসিমাকে তর্জমা করে পড়ে পড়ে শোনায় কি লিখেছে। ... ...

সিজনস অব বিট্রেয়াল - প্রথম পর্ব - দময়ন্তী
বুলবুলভাজা | ধারাবাহিক | ১৪ মে ২০১৭ | ১২৫৪♦ বার পঠিত | মন্তব্য : ১৭, লিখছেন (দ, Bittu, Aditi Dasgupta)এইসময় তো বাবার ব্যাঙ্কে অনেক কাজ থাকে, চেয়ার থেকে ওঠার সময়ই থাকে না , এইসময় হঠাৎ বাবা বাড়ী এল কেন --- এইসব ভাবতে ভাবতেই যুঁইয়ের স্নান সারা হয়, গোয়ালঘরের পাশ দিয়ে ঘুরে অন্দরের ঘরে এসে ঢুকে চুল আঁচড়ায়, কাজল দিয়ে কপালে একটা টিপ পরে ছোট্ট – আধা অন্ধকার ঘরের দেরাজ আয়নায় নিজেকে দেখে একবার এপাশ ফিরে, একবার ওপাশ ফিরে। মা ঘরে ঢোকে বাচ্চুকে কোলে নিয়ে, ওকে দেখেই চাপা গলায় একবার বাইরের বৈঠকখানার ভেতরদিকের দাওয়ায় আসতে বলে। যুঁই ভারী অবাক হয়, বাইরের লোক থাকলে বৈঠকখানার দিকে ওর যাওয়া মানা তো, মা’কে প্রশ্ন করার সাহস ওর নেই, যাওয়ার জন্য পা বাড়াতেই মা’র চোখ পড়ে ওর কপালের টিপের দিকে, চাপা গলায় প্রায় ধমকে মা ওকে টিপটা মুছে বাইরে যেতে বলে। যুঁইয়ের চোখে জল আসে – কোথাও তো একটু বাইরে যায় না কতদিন হল, ইস্কুলে যাওয়াও বন্ধ, বাড়ীর মধ্যে একটা ছোট্ট মুসুর দানার মত টিপ – তাও মুছতে হবে! মা ততক্ষণে অধৈর্য্য হয়ে এগিয়ে এসে নিজের আঁচল দিয়ে ঘষে ঘষে মুছে দেয় টিপটা – একটু পিছিয়ে গিয়ে দেখে নেয় কপালে টিপের কোনও চিহ্ন থেকে গেল কিনা – বাচ্চু হাত বাড়ায় যুঁইয়ের কোলে আসবে – মা হাত টেনে নিয়ে শক্ত করে বাচ্চুকে কোলে চেপে ধরে হাঁটা দেয়। যুঁই কেমন আবছামত বুঝতে পারে কোথাও একটা কিছু গোলমাল হয়েছে, বড় গোলমাল। ... ...

প্রকৃতির রুদ্রমূর্তির কাছে সুন্দরবনের আত্মসমর্পণ বিনা আর কি কোন পথ নেই! - ডঃ দেবর্ষি ভট্টাচার্য
বুলবুলভাজা | আলোচনা : পরিবেশ | ১৫ জুলাই ২০২৪ | ৩৬৫ বার পঠিত | মন্তব্য : ৫, লিখছেন (Supriyo Mondal, দ, অরিন)কালের নিয়মে, হিংস্র মৃত্যুদানবের উন্মত্ত নেশাতে এক সময় অবসাদ এসে জমাট বাঁধে। অহর্নিশি তোলপাড়ের ক্লান্তিতে খরস্রোতা নদীর চোখ ক্ষণিকের তরে বুজে আসে। বিধ্বস্ত চরাচরে ঝুপ করে নেমে আসে শ্মশানের স্তব্ধতা। গোবর নিকানো আদুরী উঠোনময় শুধু চরে বেড়ায় স্মৃতির বিধ্বংসী খণ্ডচিত্র। সুন্দরবনের মানুষদের আছেটাই বা কি, যে হারাবে! কিঞ্চিত জমি-জিরেত, খান কয়েক গবাদি পশু, স্বপ্ন বোঝাই ডিঙি নৌকো, আর নদীর ওপারের ভয়াল বাদাবন। ... ...
- পাতা : ২৬৭২৬৬২৬৫২৬৪২৬৩২৬২২৬১২৬০২৫৯২৫৮
-
গুরুচণ্ডা৯-র গ্রাহক হোন
কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে গুরুচণ্ডা৯-র গ্রাহক হোন। গুরুচণ্ডা৯তে প্রকাশিত লেখাগুলি পেতে চাইলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যুক্ত হোন, অথবা, আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলটির গ্রাহক হোন।
- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই
- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... রমিত চট্টোপাধ্যায়, ., রমিত চট্টোপাধ্যায়)
(লিখছেন... অসিতবরণ বিশ্বাস , দ)
(লিখছেন... PRABIRJIT SARKAR, অমিতাভ চক্রবর্ত্তী)
(লিখছেন... অমিতাভ চক্রবর্ত্তী)
(লিখছেন... কচ্ছপ, Debasis Bhattacharya, Debasis Bhattacharya)
- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন
(লিখছেন... হীরেন সিংহরায়, শিবাংশু, Saktinath Mukherjee)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... অসিতবরণ বিশ্বাস , দ, aranya)
(লিখছেন... দ, Nirmalya Nag)
(লিখছেন... হীরেন সিংহরায়, পাপাঙ্গুল, মোহাম্মদ কাজী মামুন)
- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... :|:, রঞ্জন , :|:)
(লিখছেন... ., Guru, Guru)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... দীপ, দীপ , ar)
(লিখছেন... কৌতূহলী, Debasis Bhattacharya, কৌতূহলী)
- কি, কেন, ইত্যাদি
- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...
- আমাদের কথা
- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...
- বুলবুলভাজা
- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...
- হরিদাস পালেরা
- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...
- টইপত্তর
- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...
- ভাটিয়া৯
- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...
- বুলবুলভাজা গুরুচন্ডা৯-র সম্পাদিত বিভাগ। এই বিভাগে প্রকাশিত লেখা অন্যত্র প্রকাশের ক্ষেত্রে গুরুচণ্ডা৯ ও লেখকের অনুমতি ও উল্লেখ প্রয়োজনীয় । টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই । ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত ।


