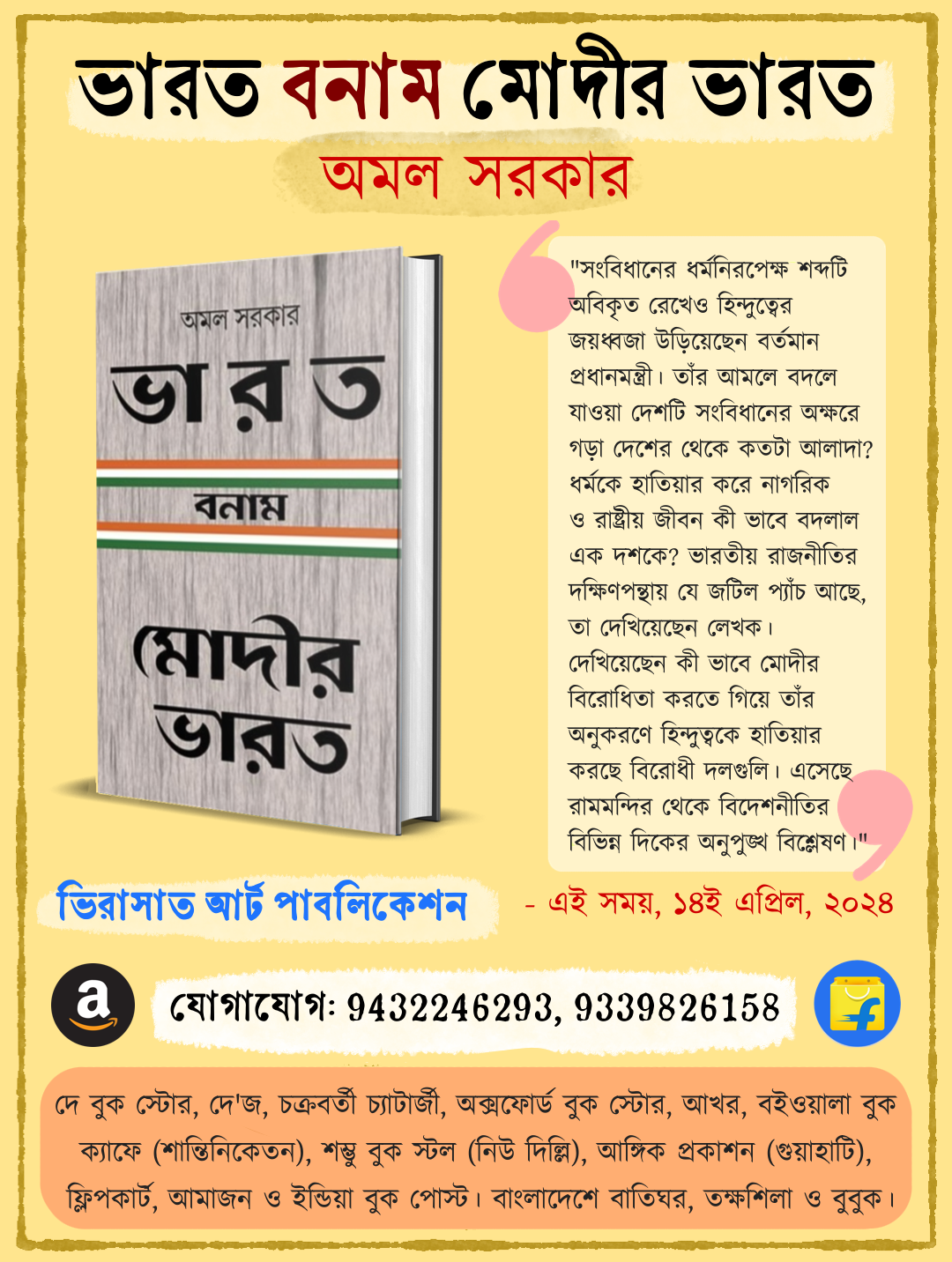- হরিদাস পাল ব্লগ

-
জেগে ওঠ (সম্পূর্ণ বইটা একত্রে)
Arin Basu লেখকের গ্রাহক হোন
ব্লগ | ২৪ মে ২০১৬ | ২৪৮৪♦ বার পঠিত - মুখবন্ধ:
গত এক বছর ধরে জ্যাক কেরুয়াকের "wake up" নামে বুদ্ধজীবনী ও সুরঙ্গমা সূত্রের ওপর লেখা একটি বইয়ের অনুপ্রেরণায় একটি বই লিখেছি। পুরো একত্রিত অবস্থায় আপনাদের জন্য এখানে তুলে রাখলাম। এক বছরের গবেষণা, একটু একটু করে লেখা। বাংলায় এর আগে হয়ত বুদ্ধদেবের জীবনী নিয়ে লেখা হয়েছে, বৌদ্ধ ধর্ম নিয়েও লেখা হয়েছে (রাহুল সাংকৃত্যায়ন, বাণী বসু (মৈত্রেয় জাতক), শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা), তথাপি যেটা নিয়ে সেভাবে লেখা হয়নি সেটা বৌদ্ধ সূত্র নিয়ে, থেরাবাদ বৌদ্ধধর্ম নিয়ে, থেরিগাথা নিয়ে। আশা করব আপনারা পড়বেন, আমার পরিশ্রম পণ্ডশ্রম হবে না।
যা মনে হয় লিখুন। এই বইটা পড়তে গেলে মূল wake up বইটা হাতের কাছে না থাকলেও চলবে, এটা স্বয়ংসম্পূর্ণ।
---
জেগে ওঠ
প্রথম অধ্যায়
পরমকারুণিক ভগবান বুদ্ধদেবের পদতলে শ্রদ্ধা নিবেদন করে শুরু করছি। বুদ্ধদেব, শূন্যতা, ও সুরঙ্গমা সূত্রকে কেন্দ্র করে এই লেখা, তা যেমন বুঝেছি, সেই মত লিখব, যতটা পারি।
এই লেখাটি জ্যাক কেরুয়াকের “wake up” নামে বইটির অনুপ্রেরণায় লেখা।
Jack Kerouac মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সান্টা বারবারায় একটি বৌদ্ধমন্দিরে গ্রথিত একটি প্রার্থনা, Dwight Goddard এর লেখা, দিয়ে শুরু করেছেন। প্রার্থনাটির ইংরেজী ভাষ্য এই রকম,
Adoration to Jesus Christ
The Messiah of the Christian World
Adoration to Gotama Sakyamuni
The Appearance Body of the Buddha
খ্রীস্টিয় জগতের আদিপুরুষ
যীশুখ্রীস্টকে প্রণাম,
বুদ্ধের অবতারকল্প
শাক্যমুনি গৌতমকে প্রণাম!
জ্যাক কেরুয়াক বুদ্ধদেবের জীবনী ও সুরঙ্গমা সূত্রের অবতারণা বিভিন্ন সূত্রের ওপর নির্ভর করে লিখেছিলেন। তাতে বৌদ্ধ ধর্মের শাস্ত্রের উদ্ধৃতি আছে। বুদ্ধদেবের জীবন কাহিনি মূলত অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত আর পদ্মলক্ষ্মী নরাসুর বুদ্ধের জীবনী থেকে নেওয়া, তবে “আলোর এই মহাসমুদ্রে” এত সহস্র নদী এসে মিশেছে যে একটি থেকে আরেকটিকে আলাদা করা তো সম্ভব নয়। এদের মধ্যে লঙ্কাবতার সূত্র, ধম্মপদ, অঙ্গুত্তরীয় নিকায়, ইতিভুত্তক (itivuttaka), দীঘ্ঘ নিকায়, মঝ্ঝিমা নিকায়, থেরাগাথা, বিনয় পিটক, প্রজ্ঞাপারমিতা হৃদয় সূত্র, সাম্যুত্ত নিকায়, চুয়াংশি, তাও তে চিং, মিলারেপার জীবন, মহাযান সংগ্রহ, এমন অজস্র লেখা।
এই লেখাটির এক মহাসূত্র — সুরঙ্গমা সূত্র কে কেন্দ্র করে। সুরঙ্গমা সূত্র যিনি মূল লিখেছিলেন, তাঁর সন্ধান পাওয়া যায় না। তিনি খ্রীষ্টিয় প্রথম শতাব্দীতে লিখেছিলেন, অবশ্য সেই সময়ে অধীত জ্ঞানসূত্রেই লিখেছিলেন নিশ্চয়ই; সেই সুপ্রাচীন ধর্মকে আসুন আরেকবার আমাদের সময়ে ফিরে দেখি।
অশ্বঘোষের কথা দিয়ে শুরু করা যাক,
“শুরু থেকে শেষ সেই মহাতাপসের কীর্তিগাথাই এই লেখার উদ্দেশ্য, যা শাস্ত্রে আছে তাই লেখা হোক, কোন রকম আত্মপ্রচার এই লেখার উদ্দেশ্য নয়।”
দ্বিতীয় অধ্যায়
বুদ্ধ কথার অর্থ যিনি জেগে উঠেছেন।
এই সেদিন অবধি, পশ্চিমের দেশগুলোতে, বুদ্ধদেবের নাম শুনলে লোকে মনে করত, টুরিস্টদের জন্যে দোকানের জানলায় সাজিয়ে রাখা, সস্তার দোকানের মিষ্টি হাসিমাখা মুখের নাদুস নুদুস গোলগাল আদুরে ভুঁড়ি বের করা আহ্লাদী এক বুড়ো, যার নাম “বুডা”। তারা জানতই না যে আসলে বুদ্ধদেব ছিলেন অসামান্য রূপবান এক যুবক, এক রাজকুমার। পিতৃপুরুষের রাজপ্রাসাদে থাকতে থাকতে একদিন হঠাৎ সেই রাজপুত্র গভীর চিন্তায় নিমজ্জিত, চোখের সামনে সুবেশা নর্তকীর দল, অথচ তাদের সে দেখেও দেখে না, যেন তারা কেউ নেই কোথাও; দৃষ্টি ভেদ করে অনন্তে প্রসারিত, তারপর …
শেষে মাত্র উনত্রিশ বছর বয়সে সংসার থেকে হাত তুলে দিয়ে দৃপ্ত যুদ্ধাশ্বে সওয়ার হয়ে সেই যে সে রাজপ্রাসাদ ছেড়ে পাড়ি দিল অরণ্যের নির্নিমেষ গভীরতায়; সেখানে খাপখোলা শাণিত তরবারীর এক কোপে ছিন্ন করে দিল তার সযত্নলালিত আজানুলম্বিত কাঞ্চণবর্ণ কেশদাম, তারপর ধ্যানমগ্ন হল সমকালীন ভারতের সাধকদের সঙ্গে; ৮০ বছর বয়সে অনন্ত সনাতন পথের, অনন্ত অরণ্যের পরিযায়ি পরম শ্রদ্ধেয় এক ছিপছিপে সন্ন্যাসীরূপে জীবনের ছেদ টেনে দিলেন চিরতরে। অথচ, মানুষটা মোটেই থলথলে গোলগাল হাসিখুশি নাদুস নুদুস তো নয়ই, বরং বলা চলে সাংঘাতিক রকমের গুরুগম্ভীর, মহাদুঃখী এক তাপস। ভারতের, প্রায় তাবৎ এশিয়ার, যীশু ।
তিনি যে ধর্মের প্রবর্তন করে গেলেন, বৌদ্ধধর্ম, অস্তিত্বের স্বপ্নে যার মহাজাগরণ, তাতে আজ লক্ষ লক্ষ মানুষ শরণ নিয়েছে। প্রাচ্যদেশের ধর্মের গভীরতা বা ব্যাপ্তির আন্দাজ আমেরিকা বা পশ্চিমের খুব অল্প মানুষেরই অবশ্য আছে। কজন লোকে জানে যে যেমন আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, ইটালি, মেক্সিকোতে খ্রীস্টধর্ম, তেমনই কোরিয়া, বর্মা, শ্যামদেশ (থাইল্যাণ্ড), তিব্বত, জাপান, লাল-পূর্ব চীন এই দেশগুলোতে বৌদ্ধধর্মের আধিপত্য।
তো এই যে তরুণ যুবরাজ, যিনি এতটাই পরমদুঃখের প্রজ্ঞায় নিবেশিত এক প্রাণ, যে, তাঁকে হারেম-ভর্তি সুন্দরীরা অবধি টলাতে পারল না, এই তিনিই গৌতম, ৫৬৩ খ্রীস্টপূর্বাব্দে সিদ্ধার্থ নাম নিয়ে ভারতের গোরক্ষপুরে শাক্যরাজবংশে রাজকুমার হয়ে জন্মেছিলেন। তাঁর মায়ের নাম, কি আশ্চর্য, মায়াদেবী (মায়া কথার অর্থ ইন্দ্রজাল); মায়াদেবী সিদ্ধার্থের জন্মের সময় মারা গিয়েছিলেন, তাই সম্পরর্কে মাসি প্রজাপতি গোতমীর কোলে সিদ্ধার্থ বড় হয়েছিলেন। ক্ষত্রিয়দের যেমনটি হওয়া উচিত, সিদ্ধার্থ যুবক বয়স থেকেই চৌকস খেলোয়াড়, ওস্তাদ ঘোড়সওয়ার; কথিত আছে যে দুরন্ত এক প্রতিযোগিতায় আর সব রাজপুত্রদের হারিয়ে সিদ্ধার্থ যশোধরার পাণিগ্রহণ করেন।
তাঁর যখন ষোল বছর বয়স, সেই সময় তাঁর যশোধরার সঙ্গে বিবাহ হয়। রাহুল নামে একটি পুত্র সন্তানও জন্মায় তাঁদের । তাঁর পিতৃদেব মহারাজ শুদ্ধোদন তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন, ও অমাত্যদের সঙ্গে মন্ত্রণা করতেন কিভাবে বছর তিরিশের সিদ্ধার্থকে এতটাই হর্ষোল্লাসে রাখা যায় যাতে ক্রমবর্ধমান গভীর দুঃখবোধ থেকে মনটাকে দূরে রাখা যায়।
কি সেই দুঃখ?
একদা, রাজউদ্যানের মধ্যে রথে চড়ে যেতে যেতে রাজপুত্র দেখতে পেলেন এক বৃদ্ধ মানুষ রাস্তা দিয়ে ধীরপদে হেঁটে যাচ্ছেন।
“এ কেমন মানুষ? শ্বেত মস্তক, স্খলিত স্কন্ধ, ঘোলাটে চোখ, শীর্ণ শরীর, যষ্টির ওপর ভর করে চলেছেন এনার শরীর কি কেবল রৌদ্রে তপ্ত ও শীর্ণ, নাকি এই অবস্থাতেই এনার জন্ম হয়েছিল? দ্রুত ঘোরাও শকট সারথি, ফিরে চল । বৃদ্ধ বয়সের কথা ভেবে দেখলে, এ কাননের শোভায় কি বা আসে যায়, জীবনের দিনগুলো যেন ঝড়ের মত বয়ে চলে, চল, চল, দ্রুত শকট ফিরিয়ে নিয়ে প্রাসাদে নিয়ে চল আমায়। “
তারপর আরেকদিন, চতুর্দোলায় মৃত মানুষকে বয়ে নিয়ে যাওয়া দেখে রাজপুত্রের রোদন, “হে নশ্বর মানব! পশ্ব! অনুসরণকারীগণ শোকে বিহ্বল, দেখ কেমন অঝোরে কেশকর্ষণপূর্বক রোরুদ্যমান … ইনিই কি কেবল একমাত্র মৃত মানুষ, নাকি এমন আরো আছে? দেখ! শরীর ধূলায় বিলীন হবেই, অথচ দেখ সর্বত্র মানুষ কেমন অবিবেচকের মত জীবন কাটাচ্ছে; এ হৃদয় তো জড়বৎ কাষ্ঠ নয়, সে নয় পাষাণ, তবু কেন এ হৃদয় বুঝেও বোঝে না সমস্ত নশ্বর, সব বিলীয়মান …”
সেই রাতে, মহারাজের কানে এই সমস্ত কথা গেল। মহারাজ রাজমন্ত্রী উদায়ীর সঙ্গে পরামর্শ করলেন। রাজার নির্দেশে উদায়ী পুরনারীদের আদেশ করলেন তারা যেন তাদের মোহিনী মায়ায় রাজপুত্রের মন ভোলায় । কত রকম অঙ্গভঙ্গিই না তারা করলে, কাঁধের আলতো রেশমী চাদর খসিয়ে ফেলে, সর্পিল বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করে, ভ্রূ নাচিয়ে, কেউ কেউ আবার ব্রীড়াবনত অবস্থায় বক্ষস্থল থেকে গোলাপ ফুল চ্যুত করে ছদ্মরোদনে বলে উঠল, “ওগো রাজকুমার, এ শরীর কি আমার নাকি তোমার?” তবু, দুঃখের মেত্তায় রাজপুত্র অটল রইলেন। রাত গড়াল মধ্যরাত্রে। নারীগণ শ্রান্ত, অবসন্ন, কেউ দিভানে, কেউ বালিশে, ঘুমিয়ে পড়লেন। জেগে রইলেন রাজপুত্র। আর একরাশ কৌতুহল নিয়ে জেগে রইলেন মন্ত্রী উদায়ী।
“এমন তো নয় যে আমি সৌন্দর্যের মর্যাদা দিই না”, গভীর অন্ধকারে কৌতুহলী মন্ত্রীর উদ্দেশে ঘোষণা করলেন তিনি, “এমনও নয় যে মানুষের আনন্দের ক্ষমতা আমি বুঝি না, তবু; তবু, সর্বত্র আমি যে দেখি সমস্ত কিছু পরিবর্তনশীল, তাইতো আমার হৃদয় বেদনাতুর; এমন যদি হত, সবকিছু একই রকম ভাবে চলতে থাকত চিরটাকাল, প্রবহমান সময়ের, আসন্ন অসুখের, মৃত্যুর যন্ত্রণা থাকত না, থাকত না ঘৃণা, থাকত না কোন কষ্ট! ধরুন আপনি দায়িত্ব নিলেন যে এই নারীদেহের সৌন্দর্য চিরকাল একই রকম থেকে যাবে, এদের ক্ষয় হবে না, তবু, প্রেমোচ্ছাসের উল্লাসের দোষত্রুটি ধরে নিয়েও, মনকে সে তবু আটকে রাখতে পারে। তাতেই বা কি? এও তো জানি অপরাপর মানুষ বৃদ্ধ হবে, তারপর জরাগ্রস্ত হবে, তারপর তার মৃত্যু হবে, এইটুকু চিন্তা পরিতৃপ্তির যাবতীয় আনন্দ যেন কেড়ে নেয়; এইটুকু বোধ হলেই মন কেমন খারাপ হয়ে যায়, যে যাবতীয় সম্ভোগ শরীরের সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যাবে একদিন; এসব জেনে বুঝেও যে মানুষ কামিনী শক্তিতে আত্মসমর্পণ করে, তার জীবন কী পশুর জীবন। ভুলভাল, ফাঁকা, সারশূন্য, মিথ্যের লালসা!
হায় গো উদায়ী!
এইটাই যে সব শেষে মনে হয়; জন্মের বেদনা, বার্ধক্যের বেদনা, মৃত্যুর বেদনা; এই যে দুঃখ, এই যে শোক, সবচেয়ে বড় ভয় তো একেই করা উচিৎ। চোখের সামনে দেখছি সব শেষ হয়ে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, অথচ মন তাদেরই পিছে ধাওয়া করে কি আনন্দই যে পায়।
হায় এ জগৎ! কি অন্ধকার, কি অজ্ঞানতা, কেউ বোঝে না!”
এবং প্রতিজ্ঞা করলেন, “এক মহতী ধর্মের সন্ধান আমি করব এইবার। সে এমনই এক পথ, লোকজন জাগতিক যে সব পন্থা অবলম্বন করে তার থেকে স্বতন্ত্র! আমি ব্যাধি, জরা, মৃত্যুকে প্রতিহত করব, ব্যাধি, জরা, মৃত্যু মানুষের জীবনে যে দুঃখ বয়ে আনে তার বিরুদ্ধে যুঝব!”
সেই কাজ করার উদ্দেশ্যে তিনি স্থির করলেন, সে কালের সাধারণ ধর্মের প্রথা অনুযায়ী, প্রাসাদ থেকে চীরতরে নিষ্ক্রান্ত হবেন, তারপর অরণ্যের একাকীত্বে তপস্যা করবেন।
সেই মধ্যরাতে নিদ্রামগ্ন ইতস্তত ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নারীদেহের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে উদায়ীকে দেখালেন, তাদের তখন আর সেই মায়াবী সৌন্দর্য নেই; নাসিকা গর্জন করছে কেউ কেউ, নানরকমের কিম্ভুতকিমাকার ভঙ্গিতে শুয়ে ঘুমে অচেতন, যেন বিশ্বগ্রাসী-দহনে খাক হয়ে যাওয়া মরমে কাতর ভগ্নীসমা একেক জন নারী , তারা এখন ক্লান্ত-নিদ্রার্ত।
পুত্রের গৃহত্যাগ ও তপস্বীর জীবনধারণের প্রতিজ্ঞার কথা মহারাজের কানে পৌঁছল। অশ্রুসজল নয়নে মহারাজ ফরিয়াদ করলেন পুত্রের কাছে। যুবরাজ তার উত্তরে বললেন, “ওগো! আমার যাত্রাপথ আর দুর্গম কোর না! তোমার সন্তান যে এক দগ্ধ, জ্বলন্ত গৃহে বসবাস করছে, সেখান থেকে সে বেরোতে চায়, তুমি কি সত্যিই তার পথরোধ করবে! মানুষের মনে কোন বিষয়ে সন্দেহ উৎপন্ন হলে সে সন্দেহ নিরসনই যেকালে সবচেয়ে যুক্তিসঙ্গত কাজ, সেখানে যে মানুষটা জানতে চাইছে, বুঝতে চায়, তাকে নিষেধ করবে?”
এরপর সিদ্ধার্থ পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন যে এই ঘনঘোর অজ্ঞানতার তিমিরে কেবল পুত্রের কর্তব্য করে যাওয়ার খাতিরে যদি আটকে থাকতে হয়, তার চেয়ে তিনি বরং নিজের প্রাণ নিজেই হনন করবেন।
পিতা শোকমগ্ন। তা দেখে যুবরাজ স্থির করলেন রাত্রে বেরোবেন। শুধু মহারাজ শুদ্ধোদন নন, যুবরাণী যশোধরাও বার বার তাঁর কাছে ভিক্ষা চাইছিলেন যেন তিনি বৈবাহিক জীবন আর রাজকার্যের দায়িত্ব হেলায় ফেলে চলে না যান। যশোধরার কোলে মাথা রেখে সিদ্ধার্থ শুয়ে মনে মনে আপন অন্তরে রোদন করলেন, তাঁর সংসারত্যাগের যে যন্ত্রণা যশোধরাকে সারা জীবন বয়ে বেড়াতে হবে, জানতেন! তখন ভাবলেন, “এই যে আমার স্নেহময়ী মা, সেই মানুষটা যখন আমাকে গর্ভে ধারণ করল, কত না গভীর মমতায়, কত না কষ্ট সয়ে আমায় বয়ে বেড়ালো মাসের পর মাস, তারপর যেই জন্মালাম সে মারা গেল, কই, তাকে তো কেউ সুযোগ দিল না আমাকে লালন-পালন করার! একজন জীবিত, একজন মৃত, দুজনে দুপথে গেছে, কোথায় কাকে পাব? এ যেন অরণ্যে, সুউচ্চ ঘন বৃক্ষে, কত না পাখির দল সাঁঝে এসে মেশে তাদের সখা-সখীদের সঙ্গে, আবার রজনী প্রভাত হলে তারা কোথায় উড়ে যায়, কে জানে, এ জগতের মিলন বিরহ হয়তো এমনই!”
বছর তিনেকের ঘুমন্ত শিশু, রাহুলের, মুখের দিকে তাকালেন। এর বহুকাল পরে তাঁর সেই সময়ের মনের ভাব ব্যক্ত করবেন তিনি, “রাহুলও যে এক বন্ধন, এই আরেক বন্ধন আমায় ছিন্ন করতেই হবে।”
মধ্যরাতে সব কিছু প্রস্তুত হবার পর ভৃত্য কন্দককে ডেকে সিদ্ধার্থ বললেন, “ঘোড়ায় জিন লাগিয়ে নিয়ে এস কন্দক; অমৃতনগরে যেতে আমার তর সইছে না। যে পবিত্র ব্রত আমি গ্রহণ করেছি, তাতে আমার মন এখন সমস্ত পরিবর্তনের ঊর্দ্ধে লক্ষ্যে স্থির।”
নিঃশব্দে তাঁরা দুজন রাজদ্বার পেরিয়ে গেলেন। তারপর একবার, শুধু একটিবার রাজপুত্র পিছন পানে চাইলেন। শিহরণ জাগলো দেহে মনে। রাজপুত্র ঘোষণা করলেন, “যদি জন্ম, জরা, মৃত্যু জয় না করতে পারি, এপথে আর ফিরব না!”
সেই রাতে অরণ্যপথে প্রভু ভৃত্য দুজনে চললেন। রাত ভোর হয়ে এল। প্রত্যূষে একজায়গায় এসে দুজনে ঘোড়া থেকে নেমে বিশ্রাম নিলেন। ঘোড়ার পিঠ চাপড়ে রাজপুত্র তাকে বললেন, “খুব সেবা করলি রে, অনেকক্ষণ, অনেকদিন ধরে আমাকে বয়েছিস।” পরে কন্দকের উদ্দেশ্যে বললেন, “যতক্ষণ ঘোড়ায় চড়ে এলাম, ততক্ষণই তুমি আমার পিছু পিছু এলে কন্দক, তোমার কাছে আমি ঋণী — আমি শুধু তোমায় এতদিন বিশ্বস্ত মানুষ বলেই জেনেছি — আজ তো আর শুধু কথার কথায় তোমায় বেঁধে রাখতে পারব না, তাই তোমায় বলি, আজ থেকে আমাদের প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক শেষ হয়ে গেল; এই নাও আমার অশ্ব, এই অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে ফিরে যাও; আমি তো সারারাত ধরে যেখানে যেতে চেয়েছিলাম সেখানেই এসে পৌঁছলাম।“
কন্দককে নিতান্ত বিষন্ন ও দুঃখিত দেখে রাজপুত্র তার হাতে একটি মহামূল্যবান রত্ন দিলেন, দিয়ে বললেন, “কন্দক! এই রত্নটি তুমি রাখ, একে নিয়ে আমার পিতৃদেবের কাছে যাবে, গিয়ে শ্রদ্ধাভরে তাঁকে প্রণাম করে এই রত্নটি তাঁর সামনে রেখে দেবে, এই রত্নটি তাঁর আর আমার অন্তরের নৈকট্যের প্রতীক। তারপর, আমার হয়ে তাঁকে বোল যেন তিনি আমার প্রতি যাবতীয় হৃদয়দৌর্বল্য পরিহার করেন, আর এও বোল যে, আমি জন্ম, জরা, মৃত্যু অতিক্রম করব বলেই গহন অরণ্যে কঠোর জীবনে প্রবেশ করেছি; আমি কিন্তু এ কাজ স্বর্গীয় কোন এক পুনর্জন্ম চাই বলে করিনি, আবার হৃদয় কঠোর বলেও করিনি, আমার কারো প্রতি কোন বিতৃষ্ণা নেই, আমি শুধু পরমাগতি চেয়েছি, চেয়েছি এক মহানিষ্ক্রমণ ।
“আমার প্রবল পরাক্রমশালী পূর্বপুরুষগণ মনে করতেন তাঁদের প্রতিষ্ঠিত রাজসিংহাসন অনড়, অপরিবর্তনীয়; তাই তাঁদের রাজৈশ্বর্য আমার হাতে তুলে দিতে চেয়েছিলেন; আমি, কেবল ধর্মের কথা ভাবতে ভাবতে সেসব দূরে সরিয়ে দিলাম, কারণ ধর্মসাধনের ঐশ্বর্য অর্জনেই আমার আনন্দ!
“হয়ত ভাবছ, আমার বয়স অল্প, আমি নেহাতই অপরিপক্ক, আস্পৃহার সময় এখনো আসেনি, তবে জেনো প্রকৃত ধর্মের আস্পৃহায় অসময় বলে কিছু নেই। সকলই অনিত্য জীবনের কিছু খেলা, জীবনের প্রতি মৃত্যুর যে বিতৃষ্ণা, তা কোনদিনই আমাদের পিছু ছাড়ে না, আর তাই, আজকের দিন, এই মুহূর্তকেই আমি বেছে নিয়েছি, এখনি, এই মুহূর্তটিই, আস্পৃহার সময়।”
বেচারা কন্দক! সে তখন কাঁদছে।
“নিজেকে নিজেই সান্ত্বনা দাও কন্দক, এ নিয়ে দুঃখ কোর না; প্রতিটি প্রাণী, যে যার নিজের মত করে, মূর্খের ন্যায় তর্ক করে যাবে যে এ জীবন নিত্য, অপরিবর্তনশীল, আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করবে যে আমি যেন আত্মীয় স্বজন পরিত্যাগ না করি; অথচ, মৃত্যুর পরে অশরীরি অবস্থায় কে আমাকে রাখবে, তারা বলতে পারবে কি?”
উজ্জ্বল উঠতি সাধুসদৃশ কথাবার্তা, অথচ কথাগুলো এক নম্র যুবা রাজপুত্রের মুখনিঃসৃত, এমন সব কথা যে, যারা তাঁকে ভালবাসত, তাদের কাছে পাষাণের মত ভারী শোনায়। কিন্তু আর তো উপায়ও নেই; সিদ্ধার্থের সঙ্গে জাগতিক সম্পর্কের ছেদ যে টানতেই হবে।
সিদ্ধার্থ বললেন, “আদিকাল থেকে মানুষ এই ভুল করে এসেছে, সামাজিক বন্ধনে নিজেদের বেঁধেছে, প্রেমের বাঁধনে নিজেদের আটকেছে, তারপর আবার স্বপ্নভঙ্গের মত কে কোথায় ছড়িয়ে পড়েছে। আমার এই কথাগুলো জানিয়ে দিও যে, যখন আমি জন্ম-মৃত্যুর দুঃখ-বারিধি অতিক্রম করব, তার পরই আমি প্রত্যাবর্তন করব; কিন্তু আমি এও প্রতিজ্ঞা করেছি, যদি লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হই, এই পর্বত সঙ্কুল জঙ্গলেই যেন আমার শরীর বিনষ্ট হয়।”
তখন শাণিত তরবারীর কোপে তাঁর সুন্দর স্বর্ণাভ কেশরাশি কর্তন করলেন, করে তাঁর তরবারী ও বহুমূল্য রত্নরাজি তাঁর প্রিয় বহুযুদ্ধের তুরগের পৃষ্ঠদেশে রাখলেন, রেখে তাকে বললেন, “এবার কন্দকের সঙ্গে চলে যাও। মনে দুঃখের উদয় হতে দিও না। হে মোর বীর যুদ্ধাশ্ব, তোমাকে ছেড়ে দিতে আমারও কষ্ট হচ্ছে। তবে তোমার কীর্তির আজ অবসান হল, তুমি নারকীয় জন্ম হতে দীর্ঘ মুক্তি পেলে !” তারপর সিদ্ধার্থ করতালি দিয়ে ভৃত্য ও অশ্ব উভয়কে বিদায় জানালেন। অতঃপর, রিক্তহস্ত, মুণ্ডিত মস্তক বিজয়ী এক বজ্রদেবতার ন্যায় একাকী অরণ্যে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন।
“আমার যাবতীয় অলঙ্কার চিরকালের মত বিদায় হয়েছে, বাকী রইল পরণের রেশমী বস্ত্র, এও সন্ন্যাসীর পরিধেয় নয়!”
ছিন্নবস্ত্র পরিধান করে একটি লোক যাচ্ছিল সে পথ দিয়ে। গৌতম তাকে হেঁকে বললেন, “শুনুন, আপনার ওই পোশাক আমার ভারি পছন্দ হয়েছে, যদি কিছু মনে না করেন, আপনার বস্ত্র আমাকে দিন, আর আমার বস্ত্র আমি আপনাকে এর বিনিময়ে দিয়ে দিচ্ছি।” এই লোকটিকে গৌতম প্রথমে ভেবেছিলেন ব্যাধ, আসলে তিনি একজন সাধু, মুনি। পোশাক বিনিময়ের পরই গৌতমের খেয়াল হল “এ তো সাধারণ বেশ নয়। ইহজাগতিক বৈষয়িক মানুষ তো পরবে না!”
একাগ্রচিত্তে ঘুরতে লাগলেন। দিনের শেষে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত বোধ করলেন। সে কালের প্রথা অনুযায়ী, গৃহহীন মানুষের যা করণীয়, গ্রামের পর্ণকুটিরে দ্বারে দ্বারে ঘুরে অন্নভিক্ষা করতে লাগলেন। রাজপুত্র ছিলেন, রাজকীয় পাকশালার প্রধান-পাচকের হাতের রান্না করা শ্রেষ্ঠ খাবার খেতে অভ্যস্ত ছিলেন, তাঁর কেতাদুরস্ত অভিজাত জিহ্বায় যখন গরীব ঘরের সামান্য খুদকুড়োর স্বাদগ্রহণ করলেন, থুথু করে ফেলে দিতে লাগলেন। অমনি বোধ হল, এ কি অন্যায় কাজ, তখন যত কষ্ট হোক, জোর করে পুরো খাবারটুকু খেয়ে নিলেন। দান বলে তাঁকে যা দেওয়া হবে, নিতান্ত খারাপ হলেও তাকে অবহেলা অশ্রদ্ধা করা হবে না।
ধর্মে উৎসর্গীকৃত যে জীবন, পরম শান্তির সন্ধানে যার যাত্রা, সেই চিরন্তন সত্যের স্বাদ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর স্বাদ আর কিছুই নেই! ইহজাগতিক যাবতীয় হার্দিক মানসিক সম্পর্ক মিটে গেছে, এখন জিহ্বার রসনার বন্ধনে আবদ্ধ থাকার সময়ও গত হয়েছে। একদা যে মানুষটির মাথায় তৎপর অনুগামীরা শ্বেতশুভ্র ছত্র ধারণ করত, যে মানুষটির পরিধানে ছিল রেশমের মহামূল্যবান পোশাক, আজ সেই মানুষটিই ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করে, যৎকিঞ্চিৎ আহার শেষে, নতমস্তকে হৃষ্টচিত্তে রৌদ্রতপ্ত অরণ্যপথে একাকী চলেছেন।
এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে নানান জনের কাছে সিদ্ধার্থ আলারা কালামার সন্ধান করতে থাকলেন। আলারা কালামা অতি বিখ্যাত সন্ন্যাসী, তাঁর সম্বন্ধে কত কিছু শুনেছিলেন। ইনি পরে সিদ্ধার্থের গুরু হবেন। আলারা কালামা শূন্যতার শিক্ষা দিতেন। তার সঙ্গে চূড়ান্ত আত্মপরিযাতনা অবলম্বন করতেন। দেখাতে চাইতেন যে তিনি যাবতীয় শরীরবোধের উর্দ্ধে বিচরণ করতে সক্ষম। শাক্যবংশের এই নতুন যুবক সন্ন্যাসীও মহোৎসাহে আলারা কালামার পদানুসরণ করতে লাগলেন। বহুকাল পরে শিষ্যদের কাছে তাঁর এই সময়কার চূড়ান্ত আত্মপরিযাতনার দিনগুলোর কথা স্মরণ করবেন। বলবেন যে, “আমি সেই সময় শৈবাল, ঘাস, গোময় আহার করে শরীর ধারণ করতাম, বন্য ফলমূল, গাছ থেকে যে ফলটুকু নিজে থেকে মাটিতে পড়ত তাই খেয়ে জীবন কাটাতাম, কেশ আর কুশ পরিধান করে থাকতাম, শ্মশান মশান ছাইগাদা থেকে যা তা ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো পেতাম সেই সব পরে থাকতাম, বন্যপ্রাণীর ফেলে যাওয়া চামড়া গায়ে জড়িয়ে রাখতাম, ঘাসপাতা, বল্কল, জন্তু-জানোয়ারের লেজের টুকরো, পেঁচার ডানার পালক, যখন যা যা পেতাম তাই দিয়ে নিজের নগ্ন শরীর কোনমতে ঢেকে রাখতাম। টেনে টেনে নিজের চুল দাড়ি ছিঁড়ে ফেলতাম, মাথা, মুখ, দাড়ি গোঁফ থেকে চুল রাখব না এই প্রতিজ্ঞা করেছি সেই সময়। একবার ভাবলাম কেবল দাঁড়িয়ে থাকব, বসব না, শোব না। আবার একবার ভাবলাম সারাক্ষণ উবু হয়ে বসে থাকব। “কন্টকবিহারী” হয়ে গেলাম একবার। যখনই পাশ ফিরে শুতে যেতাম, কন্টকশয্যায় শরীর রাখতাম — একবার ভয়ংকর দুর্গম এক জঙ্গলে গিয়ে সেখানেই রয়ে যাব মনস্থ করলাম। সে এক ভয়াবহ অরণ্য, সামান্য কাণ্ডজ্ঞান সম্পন্ন মানুষ সেখানে গেলেই ভয়ে রোম খাড়া হয়ে যাবে। এহেন যে মানুষ, পরে যিনি বুদ্ধ হবেন, তিনি এমন করে ছ’বছর, প্রথমে আলারা কালামার সঙ্গে, তারপরে আরো পাঁচজন ভিক্ষু-সাধুর সঙ্গে উরুভেলার কাছে তপোবনে এই সমস্ত মারাত্মক অর্থহীন সাধনা করে বেড়াতেন। তার সঙ্গে উপবাস। সে উপবাস এমন সাঙ্ঘাতিক যে, “আমার হাত পাগুলো ক্ষয়াটে শুকনো পাটকাঠির মত হয়ে গিয়েছিল, কোমরের হাড় উটের কুঁজের মতো বেরিয়ে থাকত, শিরদাঁড়া দড়ির মত পাকিয়ে গিয়েছিল, বাড়াবাড়ি রকমের উপোস করে করে পাঁজরার অবস্থা হয়েছিল পোড়োবাড়ির ছাদের মত বাঁকা। পেটে হাত দিলে শিরদাঁড়ায় হাত ঠেকত, হাত ঝাড়া দিলেও মাথা থেকে চুল খসে পড়ত।”
এমনি করে চলতে চলতে শেষে একদিন নৈরঞ্জনা নদীতে স্নান করতে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে প্রায় ডুবে যাচ্ছিলেন। তখন বোধোদয় হল, এই যে বাড়াবাড়ি রকমের মুক্তির সাধনা চলছে, এও প্রকৃতপক্ষে চূড়ান্ত রকমের অজ্ঞতার নামান্তর; দেখলেন, এ সবই অস্তিত্ব নামক মুদ্রাটির এপিঠ ওপিঠ — একদিকে চূড়ান্ত ভোগবিলাস, অন্যদিকে চূড়ান্ত ক্লেশ, উপবাস। একদিকে মাত্রাহীন, স্বার্থপরের মত, অবোধের ন্যায় বিলাস ব্যসন, বোধশক্তিরহিত; অপরদিকেও সেই বোধহীনতা, মাত্রাতিরিক্ত দারিদ্র্য-ক্লেশ-শারীরি-যাতনা নির্বোধতা, একই রকমের উল্টোপাল্টা অকারণ-অন্ধ কার্যকলাপ।
জনৈকা নারী তাঁকে দেবতা মনে করে পায়েস রান্না করে দিয়েছিলেন, সেই পায়েস আহার করে সিদ্ধার্থ বেঁচে উঠলেন। “এই যে এত ভোগান্তি, বড় খারাপ লাগে!” ঘোষণা করলেন তিনি।
সঙ্গী পাঁচ কঠোর তপস্বীর কাছে গেলেন, তাদের কাছে তাঁর উপদেশ,
“এই যে সঙ্গীরা! কেবল স্বর্গসুখ পাবে বলে বহিরঙ্গ শেষ করার তদবির করছ, নিজের শরীরের প্রতি যতরকমের বেদনাদায়ক অত্যাচার করা যায় তার কিছুই তো বাকী রাখলে না, এদিকে একটা স্বর্গীয় জন্মের খোঁজ করে বেড়াচ্ছ, আবার তো সেই ঝামেলা পোহানোর ব্যাপার, কোন এক ভবিষ্যত আনন্দের ছবি চোখে ভাসিয়ে, দুর্বল হৃদয় শুধুই মজে যায়, ডুবতে থাকে … আর সেইজন্যেই, সেই কারণেই, আমি দেখতে চাই কোন পথে শরীরকে সুস্থ ও শক্ত রাখব, যাতে খাদ্য ও পানীয়ের মাধ্যমে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সুস্থ রাখা যায়, তাতে শরীরের তৃপ্তি, প্রাণের আরাম । প্রাণে আরাম আসুক, জীবনের শান্ত সমাহিত সমতার ভাবটিকে উপভোগ করি। এই শান্ত, সমাহিত সমতাবোধটাই তূরীয় অবস্থা প্রাপ্তির চাবিকাঠি। তূরীয় অবস্থাতেই সদধর্মের প্রকৃত উপলব্ধি হয়, তারপরই জড়বন্ধন থেকে মুক্তি আসবে ।
“ইহলোক, স্বর্গলোক, নরক — ত্রিভুবনের আওতা থেকে উত্তরণ চাই আমি। যে ধর্ম তোমরা পালন করছ, এ ধর্ম তোমাদের পূর্বতন গুরুগণের কৃতকর্মজনিত উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছ। কিন্তু আমি, এই যে সব এর ওর মেলানো মেশানো জোড়াতালি দেওয়া, আমি, সেইসব যাবতীয় তালগোল পাকানো ধর্ম শেষ করতে চাই, আমি চাই এমন এক ধর্মের সন্ধান, যেখানে কোন সমাপতন নেই। সেই জন্যই, আর কোন অর্থহীন আলাপ আলোচনার, আর কোন তর্কের মধ্যে আমি নেই, চললাম, এই তপোবনে আর এক মুহূর্তও কাটাতে চাইনা।”
এইসব শুনে তো তাঁর সঙ্গী তপস্বীরা অবাক হয়ে গেলেন, বলতে লাগলেন, গৌতম হাল ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু শাক্যমুনি, এই পাঁচ কঠোর তপস্বীর প্রচলিত পন্থাকে “শূন্যে গ্রন্থি বন্ধনের প্রয়াস”, বলে তাদের সঙ্গ ছেড়ে চলে গেলেন, আত্মক্লেশী তাপস আর রইলেন না, হয়ে গেলেন পরিযায়ী পরিব্বিজক (পরিব্রাজক)।
সিদ্ধার্থ নানা জায়গায় ভ্রমণ করছিলেন, এমন সময় তাঁর পিতার সন্তাপের কথা কানে এল। ইত্যবসরে ছ’বছর কেটে গেছে, এতদিন পরে এই সংবাদে তাঁর কোমল হৃদয়ে পিতার প্রতি অপার ভালবাসার উদ্রেক হল। যে লোকটি তার পিতার শোক-দুঃখের সংবাদ বহন করে নিয়ে এসেছিল তাকে বললেন, “সবই স্বপ্নবৎ, সবই নশ্বর, সব শূন্যে বিলীন হয়ে যাবে … প্রিয়জনের ভালবাসা, সে এই বেঁধে রাখে, তো পুনরায় সে বন্ধন শিথিল হয়, এই যে ক্রমাগত দূর থেকে দূরে সরে সরে যাওয়া, কত আর এ নিয়ে দুঃখ করা যায়? এ নিয়ে যত আফশোষই হোক না কেন, তার কোন নাগাল পাওয়া যায় না। কেননা তাবৎ বস্তু সমুদায়ের কালক্রমে লয় অনিবার্য, কারণ মৃত্যুই কালের নিয়ন্তা, মৃত্যুকে দূর কর, কালও লুপ্ত হবে …
“তোমরা চাও আমি রাজা হই … বাইরের এই রূপের বিষয় চিন্তা করলে আমার অন্তর বড় বিষন্ন হয় … ঐ যে অলঙ্কারের প্রাচুর্যে শোভিত রাজপ্রাসাদ, আমি দেখি তাতে সর্বত্র আগুন জ্বলছে, ঐ যে শত শত অমৃতের ন্যায় ব্যঞ্জন, যেন স্বর্গের পাকশালায় প্রস্তুত, তাতে যেন বিষ মিশে আছে। চক্রবর্তী রাজন্যগণ, তাঁদের বিষয় বিতৃষ্ণা হতে বিলক্ষণ অবহিত আছেন যে, ধর্মে নিবেশিত জীবনের যে স্থিতি, তার সঙ্গে রাজ্যপাট পরিচালনার ঝামেলা-ঝঞ্ঝাটের কোন তুলনা চলে না। অন্তরের স্তব্ধভাব ও তার বিশ্রামই মুক্তির উৎস। একদিকে রাজসিক সম্ভোগ অন্যদিকে উদ্ধারপ্রাপ্তি, একদিকে গতি, অন্যদিকে স্থিতি, এই দুটিকে একত্র করা যায় না। আমার চিত্ত অচঞ্চল; বিষয়সম্পর্কের প্রলোভন আমি ছিন্ন করেছি, একনিষ্ঠ উদ্দেশ্য নিয়ে আমি গৃহত্যাগ করেছি।”
পথে অন্যান্য যে সমস্ত সাধু সন্ন্যাসীদের সঙ্গে দেখা হত, তাদের উপদেশ দিতেন,
“আত্মনিবৃত্তির পরম ধর্ম অনুসরণ করুন, পুরাকালে যে কথা বলা হত, তাকে অবধান করুন। পাপ হতে সন্তাপের উৎপত্তি।”
পূজ্যপাদ অশ্বঘোষ বুদ্ধের এই অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন,
“অটল উপস্থিতিতে ঋজু পদক্ষেপে তিনি নগরে প্রবেশ করে, মহাসন্ন্যাসীর প্রথানুযায়ী অন্নভিক্ষা করতেন, তৃপ্ত নিবিষ্ট মনে তদ্গত চিত্তে, কম ভিক্ষা পেলেন না বেশী ভিক্ষা পেলেন তা নিয়ে কোনরূপ চিন্তা ছিল না; যা পেতেন, মূল্যবান হোক, সামান্য হোক, তাকে ভিক্ষাপাত্রে রাখতেন, তারপর অরণ্যে ফিরে গিয়ে সেই অন্ন গ্রহণ করতেন ও তরণীর জলপান করতেন, অতঃপর আনন্দিত চিত্তে পর্বতে অধিষ্ঠান করতেন।”
পূজ্যপাদ অশ্বঘোষ লিখেছেন,
অলোলচক্ষুর্যুগমাত্রদর্শী নিবৃত্তবাক্যমত্রিতমন্দগামী
চচারভিক্ষম সা তু ভিক্ষুভার্যনিদায় গাত্রাণী চলঞ্চচিত
সিদ্ধার্থ রাজা রাজড়াদের সঙ্গে নানান বিষয়ে আলোচনা করতেন, তাঁদের নিজের মতের অনুগামী করে তুলতেন । একবার সিদ্ধার্থ অরণ্যে অধিষ্ঠান করছেন, এমন সময়ে মগধরাজ বিম্বিসার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। মহারাজ বিম্বিসারের কৌতূহল, রাজপরিবারে জন্মগ্রহণ করেও কেন একজন মানুষ রাজ্যপাট শাসন করার অধিকার ছেড়ে দেয়।
“সাধারণের মধ্যে যা দান ও বিতরণ করা হয়, তাকেই রাজ্যের প্রকৃত সম্পদ বলা যেতে পারে, কেবল রাজকোষে সঞ্চিত বিত্তই সম্পদ নয়,”, সিদ্ধার্থ বললেন, “দান খয়রাত করতে গিয়ে অর্থসম্পদ অনেকটাই বিলিয়ে গেলেও একাজে কোন অনুশোচনা থাকেনা।”
মহারাজ বিম্বিসার তবু ছাড়বার পাত্র নন, জানতে চাইলেন, এহেন মানুষ, যিনি রাজ্যশাসনের ব্যাপারে এমন সব বিধি বিষয়ে প্রাজ্ঞ, তিনি কি কারণেই বা রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করেছেন, আর কেনই বা রাজপ্রাসাদের বিলাসবহুল জীবনের আনন্দ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে রেখেছেন?
“আমি জন্ম, জরা, অসুস্থতা, মৃত্যু ভয়ে ভীত, তাই আমি মুক্তির এক নিশ্চিত উপায় সন্ধান করি। অতএব আমি পাঁচটি বাসনাকেও ভয় পাই — যে বাসনাসমূহ দৃষ্টির, শ্রবণের, স্বাদ গ্রহণের, ঘ্রাণের, স্পর্শের সম্পৃক্ত — এরা অনিত্য তস্করের দল, যারা মানুষের কাছ থেকে তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ হরণ করে মানুষকে এক অলীক জীবনের বিহারী, অস্থিরমতি করে তোলে — মানুষের জীবনের শান্তি ছত্রভঙ্গ করে প্রবল প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে।
‘স্বর্গের আনন্দই যেখানে এমন কোন প্রাপ্তব্য নয়, সেখানে মামুলি কামনা বাসনায় কি বা কাজ, উন্মত্ত প্রেমের তৃষ্ণানিবারণে যা মেলে, পরক্ষণেই ভোগের উচ্ছ্বাসে সে কোথায় হারিয়ে যাবে। এ যেন সেই সম্রাটের ন্যায় অস্থির, সসাগরা ধরিত্রীর পালনকর্তা হয়েও যিনি অতিরিক্ত কিছুর সন্ধান করতে থাকেন, ওপারে আর কি আছে তার সন্ধান, মানুষের কামনা-বাসনাও তদ্রূপ; অপার মহাসমুদ্রের তুল্য, এটুকুও জানা নেই কোথায়, কখন রাশ টানতে হয়। লোভ লালসাকে একটু প্রশ্রয় দিলেই দেখবেন শিশুর বাড়বৃদ্ধির মত সে ক্রমশ বেড়ে যেতে থাকে। যে মানুষ জ্ঞানী, যিনি দুঃখ কত তিক্ত তা জানেন, আর তাই তিনি কামনা বাসনার উৎপত্তি সমূলে নিষ্পেষিত করেন।
“এ জগৎ যাকে মহৎ গুণ বলে বিচার করে, সেও প্রকারান্তরে নিতান্তই দুঃখময়, মহারাজ!
“সমুদায় বস্তুকে মায়াবৎ জ্ঞান করে প্রকৃত জ্ঞানী তাই বাসনা কামনা রহিত; অপিচ বাসনায় নিমজ্জিত মানুষ কেবল দুঃখেরই কামনা করে। দুঃখের উন্মেষ হওয়া মাত্র জ্ঞানী তাকে পূতিগন্ধময় অস্থিবৎ পরিত্যাগ করে দূরে নিক্ষেপ করেন।
“যাকে জ্ঞানীজন কখনো গ্রহণ করার বিবেচনা পর্যন্ত করেন না, রাজা কিনা তাকেই আগুনে পুড়তে হলে পুড়ে, জলে সিক্ত হতে হলে সিক্ত হয়েও পাবার চেষ্টা করেন, সেই সম্পদ, যার সন্ধানে এত পরিশ্রম, সে যেন এক পচা গলা মাংসপিণ্ড!
“তাই প্রকৃত জ্ঞানী কখনোই ধন সম্পদ সঞ্চয় করেন না, তাতে বিষয়চিন্তায়, শত্রুভয়ে মন দিবারাত্র উদ্বিগ্ন হয়।
“ মহারাজ! কত না কষ্ট সয়ে মানুষ ধনসম্পদ লাভের পরিকল্পনা করে। বহু কষ্ট সয়ে মানুষকে সম্পদ উপার্জন করতে হয়, অথচ দেখুন, যেন স্বপ্নে প্রাপ্ত, এমন ভাবে কত সহজেই তাকে নষ্ট করা যায়; যে বস্তুর আঁস্তাকুড়ে স্থান হওয়া উচিৎ, প্রকৃত জ্ঞানী কেনই বা তিলে তিলে তাকে সঞ্চয় করে রাখতে চাইবেন! বিত্তবাসনা মানুষকে নিষ্ঠুর করে তোলে, দুঃখের তীক্ষ্ণ শলাকায় তার শরীর ভেদ করে যেন কর্কশ চাবুকের দ্বারা প্রহার করে; দীর্ঘ রাত্রি ছায়ে শরীর, অন্তরাত্মা নিংড়ে, আশা হরণ করে, লালসা যে মানুষকে অমানুষ করে তোলে।
“এ যেন মৎস্যের বঁড়শিপ্রেম!
“লোভ চায় তার চাহিদা পূর্ণ করতে, কিন্তু দুঃখের যে অন্ত নেই। আমাদের কামনা বাসনাকে তৃপ্ত করতে গিয়ে আমরা তাদের শুধু বাড়িয়েই যাই। সময় বয়ে যায়, দুঃখ বার বার ফিরে আসে।
“অতএব অজস্র বিষয়ে মাথা ঘামিয়ে কি লাভ বলুন, এতে উদ্বেগই শুধু বাড়ে। বাসনাকে তুষ্ট করতে গিয়ে যে দুঃখের উৎপত্তি, তার অন্ত করুন মহারাজ, মহাব্যস্ত জীবনযাপন হতে আত্মসংবরণ করুন, এতেই আপনার যথার্থ বিশ্রাম!”
কন্দক যে কথা সিদ্ধার্থকে বলেছিল, তেমনই মহারাজ বিম্বিসারও আর না বলে থাকতে পারলেন না, শাক্যরাজকুমার, তোমার বাপু সংসার ত্যাগের বয়স হয়নি, তুমি নেহাতই ছেলেমানুষ।
“বলছেন বটে যুবাবয়সে মানুষ ফুর্তি করুক, বৃদ্ধ হলে ধর্মচর্চা, আমি কি মনে করি জানেন, বার্ধক্যের কাল এতটাই অনিশ্চিত, যে যুবাবয়সের মত আর ধর্মপালনের শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতা থাকে না।”
বৃদ্ধ মহারাজ বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করলেন ।
“চঞ্চলতা এক শবর, আয়ু তার ধনু, ব্যাধি তার শর, জীবনমৃত্যুর মহাক্ষেত্রে সে জীবিতের মৃগয়া করে; যখনই সে সুযোগ পায়, আমাদের প্রাণহরণ করে, বৃদ্ধ বয়সের জন্য কেই বা অপেক্ষা করে থাকবে?”
ধর্মপালন বিষয়ে সিদ্ধার্থ মহারাজ বিম্বিসারকে প্রাণিহত্যা ও বলিদান থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিলেন, “প্রাণহত্যা করে ধর্মসাধন, মানুষের এ কেমন প্রেম? বলিদানের ফল যদি অক্ষয় হয়, তাহলেও প্রাণিহত্যা অনুচিৎ, তাহলে বিচার করে দেখুন ক্ষণস্থায়ী ফলের আশায় সে কাজ বোধকরি আরো কত অন্যায়! জ্ঞানীজন প্রাণহত্যা থেকে বিরত থাকেন। বায়ুপ্রবাহের ন্যায়, তৃণশীর্ষে বারিবিন্দুর ন্যায়, অনাগত ভবিষ্যতের ফলাফল ক্ষণস্থায়ী ও অনিশ্চিত নিয়মের বশবর্তী, আমি তাকে তাই দূরে সরিয়ে রাখি, কারণ আমি যে যথার্থ মুক্তি চাই!”
মহারাজ বিম্বিসার উপলব্ধি করলেন যে তাঁর চেতনার উদ্বোধন তাঁর অর্জিত সম্পদের অগ্রে, অতএব এক্ষেত্রে চেতনার গুরুত্বই অধিক। তিনি মনে মনে চিন্তা করলেন, “অনুধাবনের সময় নিতান্তই কম, আমি যেন ধর্ম রক্ষা করতেই সক্ষম হই।” মহারাজের চক্ষুন্মীলিত হল, দিব্যজ্ঞান লাভ করলেন, তদবধি গৌতমের আজীবন সমর্থক হয়ে রইলেন তিনি।
গৌতম যে বনে তপস্যা করতেন, সেখানে অন্যন্য শীর্ষস্থানীয় ঋষি-মুনিও তপস্যা করতেন, গৌতম তাঁদের সঙ্গে নানান বিষয়ে আলাপ আলোচনা করতেন। এঁদের মধ্যে অন্যতম, আরাদা উদারামা (Arada Udarama), গৌতম তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, “মুনিবর, কোন উপায়ে জরা, রোগ, ও মৃত্যু হতে উদ্ধার পাওয়া যাবে?”
উদারামা উত্তর দিলেন, “অহং” এর পরিশুদ্ধিতেই প্রকৃত মুক্তি। এ ছিল সেই সময়ের সনাতনী শিক্ষা: তখনকার দিনে বলা হত যে “পুরুষ”, অবিনশ্বর আত্মা, আত্মন, পরমাত্মা — জন্ম থেকে জন্মান্তরে ক্রমাগত পরিশুদ্ধ হতে হতে অবশেষে স্বর্গে শুদ্ধ আত্মার অবস্থাপ্রাপ্ত হন, এইটাই প্রতিগমনের উদ্দেশ্য।
শুদ্ধচিত্ত গৌতমের এ কথা শুনে মনে হল, যদি এমনটাই ধরে নেওয়া হয় যে জন্মের উৎস আর লয় থেকে কারো সত্যিকারের নিস্তার নেই, তাহলে পুরুষ ব্যাপারটা একটা খেলা বই কিছু নয়। খেলার গোলক যেমন মাটিতে লাফাতে লাফাতে ইতস্তত ঘুরে বেড়ায়, যখন যেরকম অবস্থার মধ্যে পড়ে, স্বর্গ, নরক, মর্ত্য, যেখানে যেমন। অথচ “জন্ম” হলে মৃত্যুও অনিবার্য — এইখানেই যে ক্ষয়, ভয়, সব কিছুই যে পরিবর্তনশীল।
গৌতম বললেন, “আপনি যে বলছেন, অহংবোধ পরিশুদ্ধ হলেই তৎক্ষণাৎ প্রকৃত মুক্তি; আবার যেখানেই কার্য-কারণের একত্র সংযোগ দেখি, সেখানেই যেন জন্মের প্রতিবন্ধকতায় ফিরে যাবার একটা ব্যাপার থাকে; ধরুণ বীজের মধ্যে যে প্রাণ নিহিত; যখন মনে হয় যে ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু সব মিলে তার অন্তর্নিহিত প্রাণকে বুঝি শেষ করে ফেলেছে, সে-ই আবার যখন উপযুক্ত পরিবেশ পায় পুনর্জীবিত হয়ে ওঠে। তার এই বেঁচে ওঠার পেছনে এমন কোন কারণ নেই, যার বহিঃপ্রকাশ আপনি দেখতে পাবেন, কিন্তু বেঁচে থাকার অন্তর্নিহিত বাসনাই তার পুনর্জীবনের কারণ; যে বেঁচে ওঠে, তার আবার মৃত্যু হবে, যেন মরার জন্যই তার বেঁচে ওঠা। সেই রকম, যাদের তথাকথিত মুক্তি হল, (তাদের আবার কোন না কোন সময় বন্ধন হবে), অহংবোধের ধারণা আর জীবিত প্রাণী, সেভাবে দেখলে প্রকৃত মুক্তি আর তাদের মেলে না।”
প্রজ্ঞা আর করুণা তাঁর মধ্যে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশের সময় যত এগিয়ে এল, ততই এই যুবা সন্ন্যাসীটি লক্ষ্য করলেন সমুদায় বস্তু — তপোবনে উপবিষ্ট সাধু, গাছপালা, আকাশ, আত্মা-সম্পর্কে ভিন্ন মত, নানান রকমের আত্মবোধ — সমস্তই যেন একত্রিত শূন্যতা, সমস্তি যেন কোন এক কল্পনার পুষ্প — চারিদিকে অবিভেদ্য একতা, সে একতা সর্বব্যাপী, অন্তঃসলিলা বিশুদ্ধ এক স্বপ্নময়তা।
অস্তিত্বকে দেখলেন যেন প্রজ্জ্বলিত দীপশিখা; প্রদীপের আলোর শিখা আর সেই আলোর নির্বাণের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। একই সঙ্গে দীপের আলো যেমন জ্বলতে থাকে, এই উজ্জ্বল আলোই তার নির্বাপণের কারণও বটে। দুই-ই এক।
দেখলেন, পরমাত্মার অস্তিত্বের ধারণা অর্থহীন। এ যেন একটা খেলার গোলকের সত্তার বিধেয় নির্ণয়ের খেলা, হাওয়ায় যে গোলকটি এলোমেলো, এদিক ওদিক ঘুরপাক খেতে থাকে, অনেকটা কেউ যেন ইচ্ছে করে দুঃস্বপ্ন দেখে যাচ্ছে, দেখেই যাচ্ছে, ভয়াল দুঃস্বপ্নের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে, অথচ বুঝছে না যে পুরোটাই মনের মায়া।
গৌতম লক্ষ্য করলেন যে বুদ্ধের নির্বাণকল্পের মধ্যে একটা শান্তির, স্থিতির ব্যাপার আছে। নির্বাণ মানে নিভে যাওয়া, যেমন একটা প্রদীপের আলোর নির্বাপণ। কিন্তু বুদ্ধ যে অর্থে নির্বাণের কথা বলেন, তা অস্তিত্বের অতীত, তাকে অতিক্রম করে যায়। বুদ্ধের নির্বাণের ধারণায় প্রদীপের আলোর অস্তিত্বও নেই, তার অনস্তিত্বও নেই। এবং ব্যাপারটা শুধু প্রদীপের শিখার নয়, তাবৎ বস্তুর, অবিনশ্বর আত্মার, সমস্ত কিছুর ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে। এমনকি নির্বাণও নয়। প্রদীপের কথা বললে, প্রদীপের আলোকশিখাকে সংসার ধরা যাক (ইহজগৎ), প্রদীপের নির্বাপিত শিখাকে নির্বাণ বলা যাক (মরজগৎ) — বুদ্ধের নির্বাণ কিন্তু এ দুটো অবস্থার একটাও নয় — বুদ্ধের নির্বাণ এসমস্তের উর্দ্ধে , আমাদের সবরকম প্রতিষ্ঠিত ধ্যানধারণার অতীত একটা সদাজাগ্রত অবস্থা!
সিদ্ধার্থর ঠিক আরাদা উদারামার ধারণা যে “অহং” বা “আমি” কে মুছে দিলেই স্বর্গের পবিত্রতা অর্জন করা হবে এ ভালো লাগেনি। সিদ্ধার্থ বস্তুনিচয়ের মধ্যে “আমি” ব্যাপারটাকে ধরতেন না। যার জন্য কাউকে কিছু শুদ্ধিকরণ করার নেই। এই স্বর্গের পুরো ধারণাটি স্বপ্নের জগতে বিচরণ করার মত। তন্মাত্র (“সৎ মন”) মনের পরিপ্রেক্ষিত থেকে দেখলে সমস্ত বস্তু, সবকিছুকে মনে হবে হাওয়ায় কেউ যেন মায়া-প্রাসাদ তৈরী করেছে।
“আরাদা যা বলছেন মন থেকে মানতে পারছি না। যাই, দেখি আরো ভালো একটা ব্যাখ্যা খুঁজে বার করি।” গৌতম খুঁজে বার করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। এক মনীষীর ভাষায়, “মানুষের মধ্যে, প্রকৃতির মধ্যে খুঁজে বেড়াচ্ছেন, পাচ্ছেন না, অথচ দেখ! এর উত্তর লুকিয়ে আছে তাঁর আপন হৃদয়ে!”
“সুধন্য তপস্বী” বুদ্ধগয়ায় গেলেন। আর তখনি তাঁর ওপর আদি বুদ্ধদের সুপ্রাচীন স্বপ্ন যেন ভর করল। সেখানে তমালবন, আম্রকুঞ্জ, ও বটবৃক্ষের পানে একমনে চেয়ে ধ্যানস্থ হলেন। দ্বিপ্রহরে ঝিরি ঝিরি বায়ু বইছে, সিদ্ধার্থ সেই সব বৃক্ষশাখার তলায় একা একা তন্ময় হয়ে হেঁটে যাচ্ছেন, মনের কোণে কোথাও বোধ হচ্ছে ভারি রকম কিছু একটা হতে চলেছে। বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠাতা গৌতম তথাগতের সুপ্রাচীন লুপ্ত পথ খুঁজে বের করেছিলেন মাত্র, পৃথিবীর আদিমতম শিশিরবিন্দুটির পুনরায় উন্মোচন হয়েছিল তাঁর হাতে; পরম করুণাঘন আঁখি মেলে একটি মরাল যেন কমল-সরোবরে ধীরে ধীরে ডানা মেলে নেমে এল, এবারে সেখানেই সে স্থিত হবে।
সেই তরু!
যে তরুতলে তিনি বসবেন বলে তাবৎ বুদ্ধ-জগৎ ও সমুদায় বুদ্ধ-বস্তুদের কথা দিয়েছিলেন, সেই সব বুদ্ধনিচয়, যারা দশদিকে ‘অ’-বস্তুর দীপ্তমান অনুভূতি নিয়ে সর্বত্র দেবদূত আর বোধিসত্ত্বরূপে বিরাজমান; তাঁরা এখন অদৃশ্য পতঙ্গের মত শূন্যতার গর্ভ অভিমুখে মহাউপাসনার অনন্তযাত্রায় চলেছেন ।
“অত্র সর্বত্র, আকাশপাতাল সব এখানেই এক হয়েছে”, সন্ন্যাসী অন্তরে অনুভব করলেন।
দূরে একটি লোক ঘাস কেটে নিয়ে যাচ্ছিল, তার কাছ থেকে কিছুটা টাটকা নরম ঘাস চেয়ে নিলেন। গাছের তলায় সেই ঘাস বিছিয়ে দিলেন। তারপর সেখানে ধ্যানস্থ হলেন। সাবধানে হাঁটু মুড়ে ঋজু শরীরে উপবিষ্ট হলেন। উপবেশন করে ধীরে ধীরে সামনে পিছনে দুলতে লাগলেন, যেন এক ঋজু, অটল মহানাগ । নিজের কাছে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করলেন, “যতদিন না বাসনার সংশ্লেষ থেকে মুক্ত হব, যতদিন না এ অন্তরাত্মা দুঃখ জয় করবে, ততদিন এই স্থান থেকে উঠব না!”
অস্থিচর্মসার যদি হতে হয়, কাকপক্ষীতে যদি ঠুকরে শেষ করে দেয়, তবু যতদিন না বিশ্বরহস্য উন্মোচন করতে পারবেন, ততদিন এই দেবতুল্য মানব বটবৃক্ষের তলায় বিছানো তৃণাসন থেকে উঠে দাঁড়াবেন না, এই তাঁর পণ। দাঁতে দাঁত লাগিয়ে তাতে জিব দিয়ে চেপে ধরলেন, তেজোময় ধীশক্তিকে দাবিয়ে রেখে, আপন অন্তরের দৃষ্টি ও অনুভূতিবোধকে প্রবাহিত করলেন অন্তরপানে। হাতে হাত, শিশুর মত মন্দ শ্লথ নীরব শ্বাসপ্রশ্বাস চলছে, দুই চোখ বন্ধ, অনড়, অবিচল। ধ্যানমগ্ন হয়ে আছেন।
তখন, সেই সোপানে সন্ধ্যার নরম আলো ছড়িয়ে পড়েছে, আবছায়া নামছে চরাচরে।
সারা জগৎ থরোথরো কাঁপে কাঁপুক, এই স্থান অটল, অবিচল থাকবে।
ভারতবর্ষে তখন বৈশাখ মাস, গোধুলি লগ্ন, স্বর্ণালী বাতাস বইছে, ঈষদুষ্ণ, স্বপ্নময় পরিবেশ। প্রাণীকূল ও জগৎসমুদায়ের নিঃশ্বাসে মেশানো দিবাবসানের সতত মানসিক নীরবতা ।
“রাত্রির মধ্যযামে, দেবদূতগণ যে প্রজ্ঞার অধিকারী, সেই প্রজ্ঞায় বুদ্ধ উপনীত হলেন। জগতের সমস্ত প্রাণীর প্রতিচ্ছবি তাঁর সামনে যেন আয়নায় প্রতিবিম্বিত হল; মৃত্যুর নিমিত্ত প্রাণীরা পুনঃপুন জন্মগ্রহণ করে, উচ্চ নীচ, ধনী দরিদ্র, সৎ বা অসৎ, যে যার কৃতকর্মের ফলহেতু, দুঃখ বা সুখভোগ করে”
“তিনি দেখলেন কিভাবে অসৎ কর্মে মন অনুতপ্ত হয় ও সেই অসততার প্রায়শ্চিত্ত করার অজ্ঞাত আগ্রহ ও ইহজগতে পুনরাবির্ভাবের তেজ সঞ্জাত হয়: অন্যদিকে কোন প্রকার সন্দেহ ও অনুতাপ না রেখেই কিভাবে সৎকর্ম জ্ঞানমার্গে বিলীন হয়ে যায়।
“দেখলেন পশুযোনিতে জন্মের কি ফল; কেউবা শুধু তাদের চর্ম বা পিশিতের কারণে মৃত্যুবরণ করে, কেউ কেউ তাদের শৃঙ্গের, কেশের, অস্থির, পক্ষের কারণে; কেউ হত হয় বন্ধু-আত্মীয়ের পারস্পরিক দ্বন্দে বিদীর্ণ হয়ে; কেউবা ভারবহন করতে করতে প্রাণত্যাগ করে, কারো প্রাণ যায় অঙ্কুশতাড়িত বিদ্ধ অবস্থায় । তাদের ক্ষতবিক্ষত শরীর বেয়ে অঝোরে রক্তক্ষরণ হয়ে চলেছে, শুষ্ক ক্ষুধিত শরীর — তবু কোন উপশম নেই, তারা পারস্পরিক সংগ্রামে রত, শরীরের শেষ শক্তিটুকুও কে শুষে নিয়েছে। আকাশে উড্ডীয়মান বা গভীর জলে নিমজ্জমান, মৃত্যুর হাত থেকে কারো নিস্তার নেই।
“আরো দেখলেন, যাদের মানুষরূপে পুনর্জন্ম হয়েছে, ক্লেদাক্ত, পূতিগন্ধময় শরীর, অবর্ণনীয় যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে যাদের দিনযাপন, জন্মবস্থা থেকে যারা শঙ্কায় কম্পমান, নমনীয় শরীরে যা কিছু স্পর্শ করে তাতেই যন্ত্রণাবোধ, যেন কেউ শাণিত ছুরির ফলায় খান খান করে তাদের কেটে ফেলছে”
এই যে কণ্টকময় উপত্যকা, যাকে জীবন বলে জেনেছি, সে যেন এক বিভীষিকাময় দুঃসপ্ন।
“জন্ম ইস্তক মৃত্যু, পরিশ্রম, দুঃখের হাত থেকে কারো মুক্তি নেই, অথচ পুনর্বার জন্মের আকাঙ্খা, এবং জন্মানো মাত্রই যন্ত্রণাভোগ ।”
নিদারুণ অজ্ঞানতার নিপীড়নযন্ত্র নিষ্পেষণ করতে করতে নিরন্তর এগিয়ে চলে।
“তারপর দেখলেন যারা সদ্গুণসম্পন্ন হয়ে স্বর্গলাভ করেছে; সতত প্রেমের তৃষ্ণা তাদের গ্রাস করে আছে, জীবনাবসানের সঙ্গে সঙ্গেই তাদের সৎকর্মেরও অন্ত হয়, পাঁচটি চিহ্ন তাদের মৃত্যুর ঈঙ্গিত বহন করে। ঔজ্জ্বল্য হৃত হয়ে অঙ্কুর যেমন শুষ্ক অবস্থায় বিনষ্ট হয়, এই সব মানুষের পারিপার্শ্বিক আত্মীয়বন্ধুরা যত শোকই করুক, এঁদের চিরকাল বাঁচিয়ে রাখতে অপারগ।
এখন শূন্য প্রাসাদ, শূন্য প্রমোদ-অঙ্গন। একাকী নিঃসঙ্গ দেবদূতগণ ধুলিধুসরিত পৃথিবীতে উপবেশিত, প্রিয়জনের কথা স্মরণ করে রোদন ও হাহাকার করছেন। বিভ্রমের এ কি ছলনা, হায়! ব্যতিক্রম নেই কোথাও, প্রতি জন্মেই নিরন্তর বেদনা।
“স্বর্গ, নরক, বা পৃথিবী, জন্ম মৃত্যুর বারিধি এইভাবে আবর্তিত — অনন্ত ঘুর্ণায়মান আবর্তনচক্র — এই সমুদ্রে নিমজ্জিত শরীরসমূহ অস্থির ভাবে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে চলেছে! এইভাবে মানসচক্ষে তিনি জীবনের পঞ্চক্ষেত্র ও জাত প্রাণিসমূহের লয়তত্ব অবধান করলেন। দেখলেন সকলই কদলীবৃক্ষ কি জলবিম্বের ন্যায় শূন্য ও অসার, সাপেক্ষহীন! “
বোধিবৃক্ষ বা জ্ঞানবৃক্ষের তলায় গৌতম ধ্যানে বসছেন, তাঁর অধিষ্ঠানের এই শুভ মুহূর্তটি নিয়ে বহু লেখালিখি হয়েছে। এই অধিষ্ঠানে উদ্যান-ভ্রমণের যন্ত্রণা ছিল না, বরং ছিল তরুতলে নিশ্চিন্তে বসে থাকার অপার শান্তি। কোনকিছুরই পুনরুজ্জীবন হবার তো ছিলই না, বরং ছিল তাবৎ সমুদায়ের বিলয়।
সেই প্রহরে বুদ্ধের প্রতীতি হল সকল বস্তু কারণ হতে উৎপন্ন হয় তারপর তাদের লয় অবশ্যম্ভাবী, সেই জন্যই সকল বস্তু অনিত্য, সমস্তই অসুখী, সবই অমূর্ত, অবাস্তব!
তিরতির করে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে।
গৌতম অনুভব করলেন, এই জগদ্ব্যাপারের যা কিছু সব মনসিজ, মন হতেই তাদের উৎপত্তি, ঐশ্বরীয় বাস্তবতার জমিতে মিথ্যার ফাঁকি যে বীজ বপন করে, সেই বীজ থেকে তাদের জন্ম। একটা মিথ্যা স্বপ্ন, সেই স্বপ্নটা জুড়ে শুধু দুঃখ আর শোক।
“সেই অরণ্যের যত পশু ছিল, তারা স্তব্ধ ও নীরব হয়ে তাঁর দিকে অপার বিস্ময়ে চেয়ে রইল” ।
বুদ্ধের খুব প্রলোভন হচ্ছিল । একবার ভাবলেন যে উঠে অন্য কোথাও চলে যান, তরুতলে এই অনর্থক ধ্যান করার দরকার নেই; পরক্ষণেই উপলব্ধি হল যে এ সবই মারের প্রলোভন, তখন অনড় রইলেন। একবার মনে দারুণ ভীতির সঞ্চার হল। এদিকে চোখ বন্ধ তবু যেন চোখের সামনে দেখলেন পিছনে কি সব হচ্ছে, প্রায় জ্বর এসে গেল ভেবে: নানারকমের চিন্তাভাবনা মনে উদয় হল। তথাপি, শিশুদের খেলতে দেখলে মানুষ যেমন অবিচল থাকে, তিনি তেমনি অবিচল রইলেন; এইসব মানসিক সংশয় আর উৎপাত মনে উঠতে দিলেন, বাধা দিলেন না, তারা বুদ্বুদের মত একবার করে উদয় হল, আবার মনসমুদ্রের শূন্যতায় বিলীন হয়ে গেল।
রাত হল।
বুদ্ধ শান্ত নীরব রইলেন, অতীন্দ্রিয় গভীর ধ্যানে প্রবেশ করলেন। সর্বপ্রকার বিমলানন্দবোধ একের পর এক তাঁর নয়নের সমুখ দিয়ে চলে যেতে লাগল। রাত্রির প্রথম প্রহরে বুদ্ধ সম্যক দৃষ্টি প্রাপ্ত হলেন (সম্মা দিত্তি), সমস্ত পূর্বজন্মের স্মৃতি তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল।
“অমুক স্থানে, অমুক নাম নিয়ে প্রথম জন্মের পর ক্রমাগত নিম্নগামী হতে হতে এই বর্তমান জন্মে আসা, এভাবে নিজের সহস্র সহস্র জন্মের ও মৃত্যুর জ্ঞান হল”
অস্তিত্বের সারাৎসার এর মূলতত্ত্ব যাঁর আয়ত্তে, তাঁর উজ্জ্বল, রহস্যময়, মানস-সত্তায় এমন কোন জন্মের কথাই বা বিস্মৃত থাকে? যেন তিনি সব হয়েছেন। সত্যিকারের আলাদা করে “তিনি” তো কখনো ছিলেন না, তিনি সদাসর্বত্র সর্বকালে বিরাজমান ছিলেন, কাজেই সমস্ত বস্তুই প্রকারান্তরে এক সত্তা, আর সবটাই নিখিল মানসের অন্তর্গত, কেননা ভুত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান, ত্রিকাল ব্যাপি সে-ই একমাত্র মানস।
“জন্ম ও মৃত্যু গঙ্গার বালুকারাশির মতই অসংখ্য, তাবৎ জীবের প্রতি অন্বয় চিন্তায় তাঁরও হৃদয়ে অপার করুণার সঞ্চার হল”
দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হয়েছে, জীবনের সুপ্রাচীন স্বপ্ন, বহুমাতৃত্বময় বেদনার অশ্রুজল, সেই সব সহস্র পিতৃপুরুষ যাঁরা এখন মৃত্তিকায় মিশে গেছেন, অনন্তকালের ভাই বোনেদের হারিয়ে যাওয়া দুপুরবেলা, ঘুম ঘুম মোরগের ডাক, কীটপতঙ্গের গহ্বর, শূন্যতায় অপব্যয়িত সেই সব দয়ার্দ্র অনুভূতি, ফেলে আসা কোন এক ঝিমধরা বিশাল স্বর্ণযুগ মস্তিষ্কে অনুভূতি জাগায় যে, এ চেতনা তো আজকের নয়, এই জ্ঞান বিশ্বের জন্মেরও প্রারব্ধ ।
তারপর, “পরম করুণার অনুভূতিও যখন অতিক্রান্ত হল, বুদ্ধ তখন পুনরায় সর্বজীবের কথা বিবেচনা করলেন, কেমন করে তারা জীবচক্রের ছটি অংশে পরিভ্রমণ করে, জন্ম বা মৃত্যু কোনটাই শেষ কথা নয়; সমস্তই শূন্যগর্ভ, সমস্তই কদলীবৃক্ষের কি স্বপ্নের কি কল্পনার প্রায় অলীক”
অনুভূতির এই সূক্ষ্ম কারুকর্মে বুদ্ধদেব যখন উপবেশন করছিলেন, তাঁর মুদ্রিত নেত্রে দৃষ্টির তমসার আবছায়ায় তূরীয় দুগ্ধফেননিভ উজ্জ্বল জ্যোতি যেন সপ্রভ বিরাজমান, তাঁর কর্ণকূহরে শ্রবণসমুদ্রের অপরিবর্তনীয় স্তব্ধতা, সে সমুদ্র কখনো উদ্বেল, কখনো অপসৃয়মান, শব্দের চেতনা স্মরণে মননে আসছিল, সে শব্দ যদিও অপরিবর্তনীয়, সেই শব্দের যদিও কোন হেরফের হয়নি, বুদ্ধের চেতনার কিন্তু পরিবর্তন হচ্ছিল; জোয়ার ভাঁটায় সমুদ্রের জল যেরকম মাঝে মাঝে চিড়বিড় করে বালি ভিজিয়ে দিয়ে যায় সেইরকম; সেই শব্দ কানের অভ্যন্তরেও নয়, তার বাইরেও নয় অথচ সে সর্বত্র বিরাজমান, অনঘ শ্রবণসিন্ধু, নির্বাণের অতীন্দ্রিয়নাদ, যাকে নিষ্পাপ শিশুরা শয্যায় শুয়ে শুনতে পায়, যে থাকে চাঁদের বুকে আর ঝড়ের হাহাকারের বক্ষ জুড়ে, তাকেই সদ্যজাত বুদ্ধ শুনতে পেলেন যেন কেউ শিক্ষা দিচ্ছে তাঁকে; প্রাচীন কালের ও অনাগত ভবিষ্যতের সমস্ত বুদ্ধের কাছ থেকে ভেসে আসছে এক অন্তহীন অথচ স্পষ্ট জ্ঞানগর্ভ দীক্ষামন্ত্র।
দূরে কোথাও ঝিঁঝিঁ ডাকছে; মাঝে মাঝে নিদ্রিত পাখিদের গলা থেকে অনবধানবশত কিচির মিচির ডাক; মেঠো ইঁদুরের খড়খড় শব্দ, গাছে গাছে পত্রমর্মর — অতীন্দ্রিয় শ্রবণের শান্তি এতে মাঝে মাঝে ভঙ্গ হচ্ছে বটে, কিন্তু এও দৈববশে। অবিচল, অবিভেদ্য তূরীয় শ্রবণ-পারাবারে যাবতীয় কোলাহল, যাবতীয় দৈববশ মিশে গেল, না তার বৃদ্ধি হল, না তার ক্ষয় হল, সে মহাশূন্যের ন্যায় আত্মশুদ্ধ ।
নক্ষত্রখচিত আকাশের তলে, রত্নসমাধির তূরীয়নাদের স্বর্গীয় প্রশান্তিতে মগ্ন অবস্থায় ধর্মরাজ অনড় ধ্যানমগ্ন হয়ে রইলেন।
রাত্রির তৃতীয় যাম। ইহজগতের দুঃখের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ভোরের কুয়াশা ক্রমশ গাঢ় হল।
“তৃতীয় প্রহরে তাঁর গভীর সত্যের উপলব্ধি হল। তিনি দুঃখসঞ্জাত, জীবনের জটিল গ্রন্থিতে আবর্তিত জগতের তাবৎ প্রাণিকূল, সেই সব অগণিত প্রাণ, যারা বেঁচে থাকে, বৃদ্ধ হয়, তারপর এক সময় মারা যায়, তাদের জন্য ধ্যানমগ্ন হলেন। সেই সব অগণিত লোভী, কামুক, অজ্ঞানতিমিরে আবদ্ধ অগণিত মানুষের দল যাদের শেষ পর্যন্ত মুক্তির উপায় জানা নেই, বুদ্ধদেব তাদেরও উদ্ধারের নিমিত্ত ধ্যানমগ্ন হলেন।”
ওগো, দেহের মৃত্যুর কারণ কি?
“সৎচিন্তায়, আপন অন্তরে তিনি ধ্যানমগ্ন হলেন জন্মের, মরণের, উৎস সন্ধানে।”
দেহের জন্মই দেহের মৃত্যুর কারণ। যেমন, বীজ বপণই গোলাপ ফুলের প্রস্ফুটনের কারণ।
আরো দূরে দৃষ্টিপাত করলেন, জন্ম তবে কোথা থেকে এসেছে? দেখলেন জন্ম এসেছে অন্য জীবনে অন্য কোথাও কৃতকর্মের কারণে; তারপর সেই কর্মের নির্ণয় করতে গিয়ে দেখলেন যে কোন বিধাতা তাকে আপন বিধানে বেঁধে দেন নি, এমনকি তারা স্বয়ম্ভুও নয়, না তাদের নিজস্ব কোন অস্তিত্ব আছে না তার অ-সৃষ্টি; দেখলেন, দীর্ঘ, দীর্ঘতর কারণ-শৃঙ্খলে কর্মের প্রাপ্তি, কারণের পর কারণের অতিদীর্ঘ সেই শৃঙ্খল, শ্রেণীপরম্পরায় গ্রথিত মাল্যবন্ধনে আবদ্ধ তাবৎ মূর্ততা — কী নীচ রূপ, কী রজকণা, বা বেদনা।
তারপর। বাঁশের প্রথম গ্রন্থিটি ভেঙ্গে ফেলার পরে যেমন পরপর বাঁশ আলগা করা যায়, মৃত্যুর কারণ জন্ম ও জন্মের কারণ কর্ম অনুধাবন করার পর তিনি ক্রমশ সত্যের দর্শন পেলেন; মৃত্যু জাত হয় জন্ম হতে, জন্ম জাত হয় কর্ম হতে, কর্ম জাত হয় বন্ধন হতে, বন্ধন জাত হয় বাসনা হতে, বাসনা জত হয় বেদন হতে, বেদন জাত হয় অনুভূতি হতে, অনুভূতি জাত হয় ষড় ইন্দ্রিয় হতে, ষড় ইন্দ্রিয় জাত হয় ব্যক্তিত্ব হতে, ব্যক্তিত্ব জাত হয় চৈতন্য থেকে।
কৃতকর্ম জাত হয় বন্ধন থেকে, কর্ম এক কাল্পনিক আকাঙ্খার হেতু করা হয়, যে কাল্পনিক কামনা-বাসনার বন্ধনে প্রাণী আবদ্ধ, যার নামে কৃতকর্মের শুরু, বন্ধন আসে বাসনা থেকে, স্বভাবের আগেও বাসনা, বাসনা আসে অনুভুতি থেকে। যার সম্বন্ধে কিছু জানতেন না, তাকে আপনি পেতে চান নি কখনো, তারপর যেদিন পেতে চাইলেন, সেদিন হয় যাকে পেতে চেয়েছিলেন তার সম্বন্ধে সুখানুভূতি হল, আর নয়ত না পাওয়ার দুঃখ যার থেকে দূরে থাকতে চেয়েছিলেন, বাসনা নামের মুদ্রাটির এপিঠ ওপিঠ; অনুভূতি সংবেদন থেকে এসেছিল, আঙুল পুড়ছে এই সংবেদন আর অনুভূতি একসঙ্গে তো হয়না। সংবেদন হয়েছিল কারণ চেতনা জাগানিয়া বস্তুটির সঙ্গে ষড়-ইন্দ্রিয়ের (চোখ, কান, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, মস্তিষ্ক) সংস্পর্শ হয়েছিল, আগুনের সংস্পর্শে না এলে তো আঙুল পোড়ে না;
ষড়েন্দ্রিয় ব্যক্তিত্বের কারণে জাত; বীজ যেমন পত্র-শাখা-প্রশাখায় পল্লবিত হয়, ব্যক্তিস্বাতন্ত্রও তেমনি একমেবাদ্বিতীয়ম দর্পণসম স্বচ্ছ পরম-মানস জাত হয়ে ষড়গুণসম্পন্ন হয়ে বেড়ে ওঠে; ব্যক্তিস্বাতন্ত্র আসে চৈতন্য থেকে, যে চৈতন্য বীজের ন্যায় অঙ্কুরিত হয়ে একেকটি পত্রে বিকশিত হয়, চেতনাকে বাদ দিলে কুতো বৃক্ষপল্লব?; তো, চৈতন্য আর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র একে অপরের সঙ্গে মিশে গেছে, আর কিছুই বাকী নেই; সমাপতিত কারণে চেতনা থেকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের উৎপত্তি, অবার অন্যদিকে অন্য কোন সমাপতনে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র থেকেই চেতনার জন্ম। সমুদ্রে জাহাজ ভেসে চলেছে, সেখানে জাহাজ ও মানুষ একসঙ্গে, আবার দেখ তীর আর জল একে অপরকে জড়িয়ে আছে; চেতনা ব্যক্তিত্বকে নিয়ে আসে, ব্যক্তিত্ব শিকড় প্রোথিত করে। শিকড় ষড়েন্দ্রিয়ের বহির্জগতের সঙ্গে সংস্পর্শবোধের উৎপত্তির কারণ, সেই সংস্পর্শ যা অনুভূতিকে বয়ে আনে; অনুভূতি বয়ে আনে অভিলাষ বা অনভিলাষ; অভিলাষ অনভিলাষ দুইই বন্ধনের কারণ; বন্ধন থেকে কৃতকর্মের উৎপত্তি, কৃতকর্ম থেকে জন্মের, জন্ম থেকে মৃত্যুর; তাবৎ জীবের অস্তিত্বের এ এক অনন্ত চক্র।
একে অতিক্রম করে, অস্তিত্ব-শৃঙ্খলের (নির্দান শৃঙ্খল) দ্বাদশ গ্রন্থিকে অবলোকন ও পরিপূর্ণ করার পর, বুদ্ধদেব দেখলেন এই যে চৈতন্য, যে ব্যক্তিত্ববোধের সঙ্গে সঙ্গে এত রকম সব বিপত্তিরও উৎস, সে স্বয়ং কর্ম (স্বপ্নের অবশিষ্ট অসমাপ্ত ফেলে আসা কাজ) সঞ্জাত, এবং কর্ম এসেছে অজ্ঞানতা থেকে, ও অজ্ঞানতা এসেছে মানস থেকে। যে অমোঘ অনড় বিধি কৃতকর্ম ও তার ফলকে একসূত্রে বেঁধে রাখে, কি ইহকালে কি পরকালে, কর্ম তারই মূর্ত প্রতিরূপ। মরজগতের যা কিছু, পশু, মানুষ, রাজন্যবর্গের ক্ষমতা, নারীদেহের সৌন্দর্য, ময়ুরপুচ্ছের অসামান্য রূপ, মানুষের নৈতিকতা, সব সব। কর্ম সজ্ঞান জীবের উত্তরাধিকার, যে ভ্রূণ তাকে বহন করে, যে ভ্রূণে সে পুনরায় ফিরে যাবে; কর্ম নৈতিকতার মূলে, কেননা যা ছিলাম নির্ধারণ করে যা হয়েছি। যে মানুষ জ্ঞানদীপ্ত হন, আলোকপ্রাপ্ত হন, তারপর স্তব্ধ হন, সর্বোচ্চ বোধি অর্জন করে নির্বাণপ্রাপ্ত হন, তার কারণ তাঁর কর্ম নিজেকে নিঃশেষ করেছে এবং এও তার কর্মেই বিধি ছিল; তেমনই অশিক্ষিত, ক্রুদ্ধ, লোভী, নির্বোধ মানুষের কর্মও নিজেকে নিঃশেষ করতে পারেনি বলেই এই অবস্থা, এও তার কর্মেই ছিল।
সম্যক আলোকপ্রাপ্ত হয়ে, সম্যক অবলোকনপূর্বক তিনি প্রজ্ঞায় উপনীত হলেন।
জন্মের বিনাশ হলে মৃত্যুও স্তব্ধ হবে, কর্মের বিনাশ হলে জন্ম স্তব্ধ হবে, আসক্তির বিনাশ হলে কর্ম সাঙ্গ হবে, বাসনার বিনাশ হলে আসক্তির অন্ত, চেতনার নাশ হলে বাসনার অন্ত, অনুভবের নাশ হলে বেদনের অন্ত, ষড়েন্দ্রিয়ের সঙ্গে সংযোগ ছিন্ন হলে অনুভবও শেষ হবে, ইন্দ্রিয়ে প্রবেশের পথের বিনাশ হলে, ব্যক্তিত্ববোধের ও সংলগ্ন বিষয়ের অন্ত হবে। চৈতন্যের নাশ হলে ব্যক্তিত্ববোধের অন্ত, আবার ব্যক্তিত্ববোধের অন্ত হলে চেতনারও অন্ত, চেতনার অন্তে কর্মের প্রভাব থাকে না। কর্ম গেলে স্বপ্নময় অজ্ঞানতারও অন্ত হয়, অজ্ঞানতার বিনাশ হলে ব্যক্তিমানুষের মৃত্যু; মহাঋষি এই ভাবে পরম প্রজ্ঞায় উপনীত হলেন।
এই হচ্ছে নির্দান চক্রের তালিকা:
১। অজ্ঞানতা
২। কর্ম
৩। চৈতন্য
৪। ব্যক্তিত্ববোধ
৫। ষড়েন্দ্রিয়
৬। অনুভূতি
৭। উপলব্ধি
৮। বাসনা
৯। আসক্তি
১০। কৃতকার্য
১১। জন্ম
১২। মৃত্যু
অন্তর্দৃষ্টি উন্মেষ হল, অজ্ঞানতা দূর হল, অন্ধকার রাত্রি শেষে সূর্যোদয় হল। আমাদের ইহজগতের তেজোময় উজ্জ্বল, আত্ম-অধীশ্বর বুদ্ধদেব স্থাণুবৎ উপবেশিত রইলেন, তাঁর অন্তরে এই মহাসংগীত ধ্বনিত হল,
“কত না জীবনের গৃহ আমাকে বেঁধেছে,
কতদিন তাঁকে খুঁজে পাব বলে সংগ্রাম করেছি,
সেই তাঁকে, যিনি ইন্দ্রিয়ের এই দুঃখময় কারাগার সৃষ্টি করেছেন,
অথচ, আজ, এই মন্দিরের স্রষ্টা — তুমি!
এই যে তোমায় চিনলাম, তুমি আর কখনো
এই বেদনার প্রাকার গড়ে,
কপট বৃক্ষশাখ, মৃত্তিকার ভেলা গড়ে
আমায় ভোলাতে পারবে না,
তোমার দুয়ার ভেঙে সেতু পেরিয়ে
পেয়েছি তোমায়,
মায়া দিয়ে গড়েছ যারে, অজ্ঞানতার নামে,
চললাম আমি মুক্তির পথে।”
এইভাবে মুক্ত হয়ে তাঁর অন্তরে জ্ঞান ও মুক্তচিন্তার উদয় হল, জানলেন পুনর্জন্মের অন্ত হয়েছে, উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। জগতের মঙ্গলকামনায় চতুরার্য সত্যে তিনি নতুন পথের সন্ধান দিলেন।
চতুরার্য সত্য
১। সমগ্র জীবন ক্লেশময় (অস্তিত্ব মাত্রই দুঃখ, অনিত্য, অপ্রকৃত/অবাস্তব অবস্থা)
২। দুঃখের কারণ অজ্ঞান অন্ধ বাসনা কামনা
৩। দুঃখ ও যন্ত্রণার অপলাপ সম্ভব
৪। তার পথ আর্য-অষ্টাঙ্গমার্গ
আর্য-অষ্টাঙ্গমার্গ
১। সম্যক দৃষ্টি (সম্মা দিত্তি)। — চতুরার্য সত্যকে আশ্রয় করে
২। সম্যক সংকল্প (সম্মা সংকপ্পা) — যে এই পথেই দুঃখ জয় করতে হবে
৩। সম্যক বাচ (সম্মা বাচ) — জগতের সমস্ত ভ্রাতা ভগিনীদের সঙ্গে নম্র, মর্মস্পর্শী বাক্যালাপ
৪। সম্যক কর্মান্ত (সম্মা কম্মান্ত) — নম্র, সরল, পরোপকারী, সৎ ব্যবহার
৫। সম্যক আজীব (সম্মা অজীব) — কারো কোন ক্ষতি না করে অন্নসংস্থান করাই জীবন
৬। সম্যক ব্যায়াম (সম্মা ব্যায়াম) — উদ্যম ও উৎসাহের সঙ্গে সৎপথে চলার প্রতিজ্ঞা
৭। সম্যক স্মৃতি (সম্মা সতি) — সর্বদা বিপথ গমনে যে বিপদ তার কথা স্মরণে রাখা
৮। সম্যক সমাধি (সম্মা সমাধি) — সমস্ত জীবজগতের বোধির নিমিত্ত আপন মনে একাকী ধ্যান প্রার্থনায় মগ্ন থেকে পরমানন্দ লাভ (সমাধি সমাপত্তির নিমিত্ত ধ্যান করা)
“এই জ্ঞান যখন আমার মধ্যে জাগ্রত হল, আমার অন্তরাত্মা কামনা, পুনর্জন্ম, অজ্ঞানতার প্রমত্ততা থেকে মুক্তিলাভ করল।”
যেভাবে তৃণের অভাবে অগ্নি নির্বাপিত হয়, সেইভাবে বুদ্ধ “আত্ম” রহিত হলেন; যে কাজ তিনি চাইতেন যে অন্যে করুক এখন তাই তিনি নিজে করলেন; পূর্ণজ্ঞানে পৌঁছনর পথ তিনি পেয়েছেন। উদ্ভাসিত জ্ঞানের আলোয় বুদ্ধের উপলব্ধি হল: যে পূর্ণজ্ঞান, সে যেন বয়ে আনা উপহার, তাঁর পূর্বে আগত অগণিত বুদ্ধের পথ নিখিল বিশ্বের দশ দিক, দশচক্র বেয়ে তাঁর কাছে এসেছে, তাতে চোখের সামনে যেন এক মহান জ্যোতি দৃশ্যমান হল যে সেই তাঁরা, বুদ্ধেরা, সর্বত্র আলোকিত করে মহাপদ্মসিংহাসনে সমাসীন, প্রপঞ্চ মহাবিশ্বের সর্বত্র সর্বকালে সর্বজীবের আর্তিতে তাঁরা সংবেদনশীল, পূর্বকাল, ইহকাল, পরকাল, অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যতের তাবৎ অস্তিত্বে তাঁরা বিরাজমান।
মহাসত্য নির্ণয় করলেন তিনি, অতঃপর সেই সত্যকে নিজের জীবনে উপলব্ধি করে মহাঋষি আলোকিত হলেন, সম্বোধি লাভ করে তিনি বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হলেন। এ সম্বোধি যথার্থ সম্বোধি, শুধুমাত্র অন্তরগজৎ হতে তার আত্মপ্রকাশ, সেখানে বহির্জগতের, বহির্জাগতিক ঈশ্বরের, গুরুর কোন স্থান নেই। কবি বলেছেন,
“শিরোপরি আত্মজ্যোতি ব্যতিরেকে,
মানুষকে কেউ পথ দেখায় না, কেউ দেখায়নি।”
তখন সেই প্রত্যূষে প্রভাতসূর্যের জ্যোতিকিরণ ক্রমশ উজ্জ্বল হল, অপসৃয়মান ধোঁয়াশা আর কূহেলী মিলিয়ে গেল দিনের আলোয়। চন্দ্র তারকার ক্ষীণ আলো ক্রমশ নিষ্প্রভ হল, দূর হল রাত্রির তমসাঘন অন্তরায়। বুদ্ধ তাঁর প্রথম পাঠ, শেষ পাঠ, সাবেক পুরাতন পাঠ সমাপন করলেন, মহাঋষির নিঃস্বপন সুপ্তিগৃহে প্রবেশ করে, পূর্ণ সমাধির স্থিতাবস্থায় তিনি অনন্ত সত্যের উৎসমুখে পৌঁছলেন যে, আনন্দের আদি নেই, আনন্দের অন্ত নেই, আনন্দ সদাসর্বদা সৎচিতে বিরাজমান।
এই যে বুদ্ধ সৎচিতের প্রকৃত রূপ উন্মোচন করলেন, এতে কোন বাহ্যিক দেখনদারির বহিঃপ্রকাশ ছিল না, ছিল অন্তরের নিঃস্তব্ধতা ও অপার শান্তি। সে পরম এক নিশ্চলতা, চরম এক স্থিতাবস্থা ।
তিনি এখন শিহিভুত, শীতল।
এইবার আসবে পরমসুখী মহাতাপসের জীবনের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ মুহূর্ত। বহু সংগ্রামের শেষে তিনি গভীর সত্যকে খুঁজে পেয়েছেন, এখন সেসব খুবই অর্থপূর্ণ, কিন্তু খুব পণ্ডিত জ্ঞানী ব্যতিরেকে তা সাধারণ মানুষের দুর্বোধ্য। সাধারণ মানুষ নেহাতই পার্থিব, তারা সুখের সন্ধানে ঘুরে মরে। তাদের ধর্মজ্ঞান, পুণ্যার্জন, বিষয়সম্পদের প্রকৃত রূপ অবধান করার ক্ষমতা থাকলে কি হবে, তারা সব পুতুলনাচের পুতুলের মতন। ছলচাতুরীর, অজ্ঞানতার মায়াজালে আবদ্ধ হয়ে, অনর্থক ধারণার বশবর্তী হয়ে কি যেন এক অদৃশ্য সুতোয় তারা নাচতে থাকে। এইসব অনর্থক ধ্যানধারণার সঙ্গে তাদের প্রকৃত শান্ত সমাহিত স্বরূপের কোন সম্পর্কই নেই। তারা কি পূর্বকৃত-স্বপ্নের কর্মফলের ধর্ম বুঝতে পারবে? তারা কি তাদের নৈতিক জগতে ক্রমান্বয়ে চলতে থাকা কার্য-কারণকে অবধান করতে সক্ষম? তারা কি আত্মার মতন একটা পাশবিক ধারণাকে উপেক্ষা করে মানুষের প্রকৃত স্বরূপের বিষয়কে অনুধাবন করতে পারবে? ব্রাহ্মণ-পুরোহিতদের ধরে এই যে তাদের মোক্ষলাভের প্রবণতা, এই প্রবণতাটিকে তারা কি অতিক্রম করে বেরিয়ে আসতে পারবে? এরা কি পরম শান্তির অবস্থাটিকে উপলব্ধি করতে সক্ষম? সেই শান্তির স্থিতাবস্থা, যা জাগতিক তৃষ্ণা নিবারণ করে নির্বাণের স্বর্গসুখের পথে মানুষকে এগিয়ে দেয়? চারিদিকে যা চলছে, তাতে যে সত্য তিনি উপলব্ধি করেছেন, যা আবিষ্কার করেছেন, সেসব প্রচার করা কি উচিত হবে? তারপর যদি না বোঝাতে পারেন, যদি ব্যর্থ হন, তখন? সে যন্ত্রণা কি সইতে পারবেন? এই রকম সব বিচিত্র প্রশ্ন আর সন্দেহ তাঁর মনে উদয় হল, তারপর সার্বজনীন করুণা আর সহমর্মিতায় সেসব ধারণা মিটেও গেল। তিনি, যিনি যাবতীয় স্বার্থপরতা পরিত্যাগ করেছেন, তিনি তো অন্যদের বাদ দিয়ে কেবল আপনার জন্য বেঁচে থাকতে পারেন না। পরের জন্য বেঁচে থাকার ব্রত যিনি নিয়েছেন তাঁর কাছে মানুষকে পরম সুখ অর্জনের পথ দেখানোর চেয়ে মহৎ আর কিই বা হতে পারে? সাংসারিক ব্যথা বেদনা, অশ্রু-সমুদ্রে নিমজ্জমান এই সব প্রাণী, এদের উদ্ধারের চেয়ে মহৎ আর কিছু আছে কি? জগতকে উপহারই যদি দিতে হয়, “প্রতিষ্ঠিত সত্য”রূপী ধর্মের সন্দর্শন করানো, এই জগতকে স্ফটিকের মত কাকচক্ষু স্বচ্ছ করে দেখিয়ে দেওয়াই কি সবচেয়ে মূল্যবান উপহার নয়?
পরিপূর্ণ মহামানব অপলক নেত্রে মহাবৃক্ষ, সমস্ত বৃক্ষের অধিরাজ যে বৃক্ষ, তার পানে নির্নিমেষ নয়নে চেয়ে রইলেন, “এ ধর্ম এক আশ্চর্য ও মহৎ ধর্ম”, মনে মনে চিন্তা করলেন তিনি, “আবার এদিকে গতানুগতিক জীবনের অজ্ঞানতায় প্রাণিকূল অন্ধ হয়ে পড়ে আছে, কি যে করি? এই যে এখন, যতক্ষণ বাক্যস্ফুট করছি, মানুষ কিন্তু পাপে নিষ্পিষ্ট হচ্ছে। এদের অজ্ঞাতার কারণে, যা বলব এরা কেউ শুনবে না, তার ফলে নিজেরাই শাস্তি পাবে । এর চেয়ে বরং চুপ থাকাই শ্রেয়। আজই বরং নিঃশব্দে আমার মরণ হোক!”
কিন্তু যখন স্মরণে এল কালে কালে সর্বজগতে গতাসু বুদ্ধগণ কি দক্ষতায় বিভিন্ন জন-কে পূর্ণ সহজ সত্যের দর্শন দিয়েছিলেন, তখন ভাবলেন, “নাহ, আমিও বুদ্ধচেতনার, আলোকপ্রাপ্তির উদ্বোধন করব!”
এর বহুকাল পরে গৌতম সারিপুত্ত ও অন্যান্য সন্ন্যাসীদের কাছে তাঁর বোধিবৃক্ষের তলায় সেই সময়ের কথা স্মরণ করে বলেছিলেন, “সেদিন যখন ধর্মের বিষয় ধ্যান করছিলাম, সর্বলোক হতে বুদ্ধেরা স্বশরীরে আমার সুমুখে উপস্থিত হয়ে সমস্বরে বললেন, “ওঁ! তথাস্তু! জগতের একমেবাদ্বিতীয়ম নেতা! শৃন্বন্তু! এই যে অপরাপর নেতৃবর্গের অতুলনীয় জ্ঞান ও ধীশক্তিতে উপনীত হলেন, ও তাঁদের ধ্যান করলেন, তাঁদের এই শিক্ষার এবার পুনরাবৃত্তি করুন। বুদ্ধরূপে আমারাও সেই পরম সত্য ত্রিকায়ায় (মূর্ত-কায়া, আনন্দ-কায়া, ধর্ম-কায়া) প্রকাশ করব। মানুষ স্বভাবত নিম্নগতি, তারা হয়ত অজ্ঞানতাবশত বিশ্বাস করতে চাইবে না, যে, “তোমরা সবাই বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হবে।”
“তাই আমরা আমাদের ক্ষমতাবলে ও ফললাভের উৎসাহহেতু বহু জ্ঞানীকে (বোধিসত্ত্ব-মনসত্ত্ব) জাগরিত করে তুলব”
“অগ্রজদের মুখনিঃসৃত এই মধুর বাণী শ্রবণ করে আমি আনন্দিত হলাম; চিত্তোল্লাসে সেই মুনীবরদের বললাম, “মহাতাপসগণের কথা কখনো ব্যর্থ হয়না!”
“অতএব আমিও, জগতের মহান নেতৃবর্গ যেমন বলেছেন সেই মত কাজ করব; ক্ষয়িষ্ণু প্রাণীকূলে জন্মেছি, তাই এই ভয়ংকর জগতের দুর্দশা সম্বন্ধে অবগত আছি’
“তখন মনে হল যে কাজের জন্য আমার জন্ম হয়েছে, মহতী ধর্ম প্রচার ও পরম চৈতন্যের প্রকাশসাধন, তার সময় সমাগত।
“কখনো কখনো, কোথাও কোথাও, কিভাবে যেন মহাত্মারা এ জগতে আবির্ভূত হন, তারপর তাঁদের আবির্ভাবের পর, তাঁদের অপার জ্ঞান, তাঁরা সময়ে সময়ে একই ধরণের ধর্ম প্রচার করেন।”
“এই পরম ধর্মের সন্ধান পাওয়া বড় দুর্লভ, হোক সে শত সহস্র যুগ ব্যাপী; বুদ্ধদের বাণী শ্রবণ করে তাঁদের পরম ধর্মের যথাযথ অনুসরণ করবেন, এমন মানুষ পাওয়াও দুর্লভ।
“গোলাকার মহাবটবৃক্ষে পুষ্প যেমন দুর্লভ, পাওয়া যে যায়না তা নয়, সুন্দর লাগে।”
“তবে যে ধর্মের আমি প্রবর্তন করব তা সব চেয়ে চমৎকার! যদি কেউ একে যথাযথ ভাবে শুনে, তাকে হর্ষের সঙ্গে গ্রহণ করে, তার পুনরাবৃত্তি করে, তবে সে সব বুদ্ধদেরই শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করবে।
“এ নিয়ে মনে কোন দ্বিধাদন্দ্ব রেখো না: আমি ঘোষণা করছি আমিই সেই ধর্মরাজ!”
“তোমরা আনন্দ কর যে তোমরা সবাই বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হবে!”
অতএব তথাগত, যিনি-চিত্তের-তদ্গত-অবস্থা-প্রাপ্ত-হয়েছেন, যিনি প্রাণীতে প্রাণীতে কোন বিভেদ দেখেন না, যিনি আপন, পর, বহু, কোন অস্তিত্বকে, অবিভক্ত নিখিল অস্তিত্বকেও আমল দেন না, যাঁর কাছে জগৎ এক দুঃখময় মায়া বই কিছু দ্রষ্টব্য নয়, না অস্তিত্ব না অনস্তিত্ব, স্বপ্ন থেকে জাগরিত কিন্তু স্বপ্নে কি দেখলেন তাই নিয়ে চিন্তা করেন না; অতএব তথাগত, শান্ত, স্তব্ধ, উজ্জ্বল, সর্বত্র জ্যোতি বিচ্ছুরণ করতঃ, তাঁর বোধি বৃক্ষের তপস্যাস্থল থেকে উথ্থান করলেন,ও অতুল্য সম্মানে তেজে একাকী স্বপ্নময় ধরিত্রীর উপর দিয়ে এগিয়ে চললেন, চিন্তা করতে করতে, “জাত বা অজাত, সকল প্রাণীর উদ্ধারকল্পে, যে সুপ্রাচীন প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, তাকে আজ সম্পূর্ণ করব। যারা চায়,তারা স্বকর্ণে মোক্ষ লাভের সৎপথের উপায়ের কথা শ্রবণ করুক।”
জগতের রাজধানী বারাণসী। সেই শহরের উদ্দেশ্যে তিনি যাত্রা করলেন।
পথে যেতে যেতে জনৈক পূর্বপরিচিত দিগম্বর জৈন সাধু উপকের সঙ্গে দেখা। উপক এই মানুষটিকে দেখলেন, যিনি একাকী বিশ্বের জন্মরহস্য প্রণিধান করেছেন, ভুলে যাওয়া পথ বেয়ে পুনর্বার নিয়েছেন সেই আদিম প্রতিজ্ঞা, যে প্রতিজ্ঞা মণিপদ্মের মতন এতদিন লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিল, সেই মানুষটিকে শুধোলেন, “কে আপনার গুরু যাঁর দীক্ষায় জগৎসংসার ত্যাগ করলেন?”
“আমার কোন দীক্ষাগুরু নেই,” আলোকিতজন বললেন, “নেই কোন মান্যবর সম্প্রদায়; কোন ঝলমলে চমৎকারিত্ব নেই আমার; থাকার মধ্যে আছে স্বাধ্যায়-সূত্রে প্রাপ্ত গভীর এক তত্ত্ব, যে তত্ত্বে অতিমানবিক প্রজ্ঞাবলে উপনীত হয়েছি ।
“বারাণসীর সর্বত্র খুব শিগগির অদম্য এক জীবনের দামামা বাজতে চলেছে — তবে সেখানে বসে থাকা চলবে না — আমার কোন নামযশ নেই — আমার কোন চাহিদাও নেই — নাম চাইনা, যশ চাই না, কিচ্ছু না।
“জগতের শিক্ষার প্রয়োজন, কিন্তু শিখবে যে, এমন ছাত্র ভূভারতে নেই, আমি নিজে নিজে তাকে সম্পূর্ণরূপে শিখেছি, তাই আমি তাকে বলি পূর্ণজ্ঞান |
“জ্ঞান-তরবারী দুঃখকে ধ্বংস করেছে, একে তাই জগৎ ঘোষণা করেছে চূড়ান্ত বিজয়।”
বললেন, “আমার কোন গুরু নেই। আমার সমকক্ষও কেউ নেই। আমি স্বয়ংসিদ্ধ বুদ্ধ । আমি অপার শান্তিলাভ করেছি, নির্বাণপ্রাপ্ত হয়েছি। ধর্মরাজ্যপ্রতিষ্ঠা হেতু আমি বারাণসী চললাম, সেখানে জীবন-মরণে যারা তমসাচ্ছন্ন হয়ে আছে, তাদের মঙ্গলকামনায় আমি এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের প্রজ্জলন করব। “
“আপনি কি বলতে চান জগৎ জয় করেছেন?” উপক জানতে চাইলেন।
জাগ্রতজন বললেন, “যাঁরা নিজেকে জয় করেছেন, তাঁরাই জগৎ জয়ী, আপন কামনাকে যাঁরা নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম, যাঁরা অন্যায় থেকে বিরত থাকতে জানেন, কেবল তাঁরাই এ জগতের জয়লাভের অধিকারী। আমি নিজেকে জয় করেছি, আমি পাপকে প্রতিহত করেছি, তাই আমি জগতজয়ী।
“অন্ধকারে প্রদীপ যেমন জ্বলে, নিজস্ব কোন উদ্দেশ্য ছাড়াই সে জ্বলে, সে তার নিজের জ্যোতিতেই আলোকিত, সেইরকম তথাগতের দীপক জ্বলমান, তাতে ব্যক্তিগত কোন অনুভূতি নেই, আপন জ্যোতিতে সে দীপ্যমান।”
বুদ্ধদেব বারাণসীতে গেলেন।
সেখানে ঈশিপত্তনের মৃগদাবে সেই পাঁচজন সাধু বসেছিলেন, যাদের সঙ্গে তিনি একসময় তপোবনে বৃথা তপস্যায় ছ’বছর কাটিয়েছিলেন । তাঁরা বুদ্ধকে আসতে দেখলেন। বুদ্ধদেব ধীর পায়ে চলেছেন, নম্রভাবে, দুচোখ মাটির দিকে সাবধানী দৃষ্টি মেলে, লাঙ্গলের ফলার মাপে মেপে মেপে পথ চলা, যেন ধর্মের প্রসাদী ফসল তিনি বুনতে বুনতে চলেছেন। দেখে ওঁরা ব্যঙ্গ করলেন।
“এই যে গৌতম এসেছে। গৌতম, যে কৃচ্ছসাধনের তপস্যার প্রথম শপথ ভেঙ্গেছিল। ওকে দেখে প্রণাম কোর না, সম্মান দেখিও না, এলে খাবার দেবারও দরকার নেই।”
অথচ, সম্ভ্রম জাগানো আভিজাত্য নিয়ে গৌতম যেই তাদের কাছে গেলেন, অনিচ্ছাসত্তেও তারা আসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন, যদিও স্থির করে রেখেছিলেন যে গৌতমকে কোন রকম শ্রদ্ধাপ্রদান করবেন না, তবু সম্ভাষণ করলেন, পা ধুইয়ে দিলেন, যা যা বুদ্ধ প্রত্যাশা করতে পারেন সে সব তাঁরা করলেন। বুদ্ধকে দেখে কেমন যেন বিহ্বল হয়ে গেলেন, যদিও তাঁরা গৌতম বলেই তাঁকে সম্বোধন করলেন। ভগবান বললেন, “আমাকে আমার ডাকনামে আর ডেকো না, যিনি অর্হতত্বপ্রাপ্ত হয়েছেন, তাঁকে নাম ধরে ডাকাডাকি করাটা অসম্মানজনক । বিষয়টি আমাকে কেন্দ্র করে নয়। আমার নিজের কিছু আসে যায় না যে কে আমাকে মানল না মানল, আমাকে শ্রদ্ধা করল কি করল না। কিন্তু অন্যদের ক্ষেত্রে, যিনি করুণাঘন হয়েছেন যিনি সর্বজীবের প্রতি সমদর্শী, তাদের ক্ষেত্রে, সেইজনকে নাম ধরে ডাকাটা শোভা পায় না। বুদ্ধগণ জগৎ উদ্ধার করেন, তাই সন্তানগণ পিতার প্রতি যেরূপ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে, তাঁদেরও সেইরকম শ্রদ্ধা নিবেদন করবে।“
এই বলে তিনি তাদের তাঁর প্রথম ধর্মোপদেশ দিলেন।
এই ধর্মোপদেশ “বারাণসীতে ধর্মোপদেশ”, বা ধর্মচক্রপ্রবর্তনসূত্র নামে প্রসিদ্ধ। এতে তিনি চতুরার্য সত্য ও অষ্টাঙ্গমার্গ সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করে তাদের দীক্ষিত করলেন। পূর্ণসত্যজ্ঞানী, সর্বব্যাপী ধীশক্তির অধিকারী বুদ্ধদেব সংক্ষেপে তাদের মধ্যপন্থা, বা সৎমার্গ সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন।
“হে ভিক্ষুগণ, চরম ভাব দুপ্রকার। যে মানুষ সংসার পরিত্যাগ করেছে, তাকে এই দুইপ্রকারের চরম ভাবই পরিহার করে চলতে হবে । একদিকে লোভী, ভোগপরায়ণ, বৈষয়িক মানুষের বিষয়বিলাস, আর অন্যদিকে অর্থহীন কৃচ্ছসাধন, প্রায় আত্মহননের মতন যাতে কোন লাভ নেই।
“মাছমাংস পরিহার করে, উলঙ্গ হয়ে, মাথা কামিয়ে, চুলে জট পাকিয়ে, কষায় বস্ত্র পরিধান করে, সর্বাঙ্গে ধুলো মেখে যাগযজ্ঞ করে, এসব করেও কিন্তু ,মানুষ যতক্ষণ মায়ামোহ থেকে মুক্তি না পাচ্ছে, তার মধ্যে পবিত্রতা আসবে না।
“ক্রোধ, মদমত্ততা, অকারণ জেদ, ধর্মান্ধতা, লোকঠকানো, হিংসা, অহংকার, আত্মপ্রশংসা, অন্যদের ছোট করা, নাক উঁচু স্বভাব, দুর্মতি, এইগুলোই যাবতীয় কলুষতা, মাছমাংস খাওয়া নয়।
“হে ভিক্ষুগণ, এই দুই চরম পথ পরিহার করে বুদ্ধ একটি মধ্যপন্থা আবিষ্কার করেছেন — যে পথ চক্ষু উন্মীলিত করে, যে পথে সম্বোধি প্রাপ্তি হয়, যাতে মনে শান্তি আসে, একটা উচ্চতর প্রজ্ঞার পথ, পরিপূর্ণ জ্ঞানের পথ, নির্বাণের পথ।
“মরুভূমিতে শুকনো ঘাস, রোদে পুড়ে যাচ্ছে, তায় হাওয়া লেগেছে — এবার তাতে আগুন লেগে ছড়িয়ে গেলে — সে আগুন নেভায় কার সাধ্যি? লোভ লালসা সেই প্রকার আগুন, তাই চরমপন্থা ছেড়ে আমি আমার হৃদয়ে মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছি।
“প্রদীপ জ্বালাতে হলে তেলের বদলে জল দিয়ে জ্বালানোর চেষ্টা বৃথা, ওতে অন্ধকার দূর হয় না, নষ্ট কাঠ দিয়ে আগুন জ্বালাতে গেলে সে আগুন জ্বলে না।
“যাঁর আত্মা সংযত হয়েছে, তিনি লোভ লালসা মুক্ত; অসংযমী মানুষ লোভের বশবর্তী হয়ে ইতস্তত ভ্রমণ করে, কামনা বাসনার টান নিম্নগামী, মানুষকে অপবিত্র করে।
“অবশ্য জীবনধারণের জন্য যতটুকু প্রয়োজন তা মেটানোতে কোন অন্যায় নেই। শরীর সুস্থ রাখা কর্তব্য, তা না হলে জ্ঞানের প্রদীপের সলতে রাখতে পারব না, মনকে পরিষ্কার ও দৃঢ় রাখা চাই।
অতঃপর সর্বজ্ঞজন যন্ত্রণা কি তা ও যন্ত্রণাকে নষ্ট করার যে আনন্দ, সেই আনন্দময় সংবাদের বিস্তারিত আলোচনা করলেন। কৌণ্ডিন্যের নেতৃত্বে পাঁচ সাধু, দুঃখকে পর্যবেক্ষণ করতে পারলে যে আনন্দের বোধ, এই তত্ত্ব উপলব্ধি করে, অবাক হয়ে গেলেন। তারপর তিনি তাঁদের অষ্টাঙ্গমার্গ সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন, যে পথে চলার আলোকবর্তিকা, পথ চেনানোর সঙ্গী, যথার্থ আস্পৃহা, মর্মস্পর্শী বাক্যকথন, সে পথে বাসগৃহ, যথার্থ আচার আচরণ, ঋজু চলন, কারো ক্ষতি না করে, কাউকে না ঠকিয়ে জীবিকা নির্বাহের যথাযথ পন্থা — একজন ভাল সুখী মানুষের এতেই নবশক্তিবিধান। সৎ উদ্যোগ নিয়ে সৎপথে চলার প্রতিজ্ঞা, যে পথ মাঝে মধ্যেই হারিয়ে যায় আবার তাকে খুঁজে বেরও করতে হয়। প্রকৃতির স্বরূপে (স্বপ্ন মায়াবৎ), তাতে মনোনিবেশ করে শ্বাসপ্রশ্বাসের মাধ্যমে সৎচিন্তা করা (“হে মোর ভিক্ষুগণ, প্রকৃতপক্ষে সবই একরকমের শূন্যতা, কিন্তু আপনারা কি তাতে মুক্তকচ্ছ হয়ে বিরাজ করতে পারেন?”)। আর যথাযথ ধ্যান, ধুলিমলিন পদচিহ্নের পিছনে চলতে থাকা পরিষ্কার চেতনার অপার শান্তি।
এই তো মুক্তির মন্ত্র, আনন্দসংবাদ, মধুর সত্য।
“তারপর যখন দিব্যজন সত্যরূপ রাজরথের চাকা এগিয়ে নিয়ে চললেন, দ্যাবাপৃথিবী জুড়ে এক পরমানন্দ অনুভূত হল”
“হে বুদ্ধ, আপনি যথার্থই পরম সত্যে উপনীত হয়েছেন”, কৌণ্ডিন্য বলে উঠলেন, মানসচক্ষে সহসা তাঁর সত্যের উপলব্ধি হল, তারপর অন্যান্য ভিক্ষুগণও তাঁর সঙ্গে একমত হয়ে বলে উথলেন, “আপনি সত্যই বুদ্ধ, আপনি পরমসত্যকে উপলব্ধি করেছেন!”
পাঁচ ভিক্ষু তখন দীক্ষা গ্রহণ করলেন ও এই পাঁচজন সংঘের কেন্দ্রবিন্দু হলেন। এর পর সেই সংঘে শত সহস্র মানুষ শরণ নেবেন।
বুদ্ধদেব বারাণসী গিয়ে দ্বারে দ্বারে অন্নের মাধুকরী করলেন । নীর নিম্নগতি, তাই সে জগতের সমস্ত উপত্যকা জয় করতে পারে, বুদ্ধদেবও তেমনি সকলের চেয়ে বিনয়ী, তাই তিনি জগৎ জয় করলেন। বুদ্ধদেবের সকল শিক্ষার মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান শিক্ষা তিনি নীরব থেকে শিক্ষাদান করতেন। বিশেষ করে গৃহস্থদের কাছে বুদ্ধদেবের বিনয় আর দানমাহাত্মের শিক্ষা। বুদ্ধদেবের মতন মানবজাতির রাজাধিরাজ, দীর্ঘকায় সুপুরুষ, সামান্য ভিক্ষাপাত্র হাতে তাদের খিড়কির দরজায় নতজানু হয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন, এই অবিশ্বাস্য ব্যাপার সাধারণ মানুষ নিজের চোখে দেখল, তাঁর শিশুসুলভ সারল্য অথচ মানুষকে বিশ্বাস করার এক অমোঘ শিক্ষা পেল। ভিক্ষা অন্তে ব্যস্ত রাজপথের ধারে শহরের বাইরে কোন একটা জায়গায় বুদ্ধদেব চলে যেতেন। তারপর সেখানে পাত্র নামিয়ে রেখে, ঋজু হয়ে দুপায়ের ওপর ভর দিয়ে বসে ভাবসমাধি অবস্থায় ধ্যান করতেন।
বারাণসীর জনৈক ধনী ব্যবসায়ীর যুবক সন্তান, নাম তার যশ, সে জগতের দুঃখে কাতর, হারেমের নারীদের প্রতি সে বীতশ্রদ্ধ। এমত অবস্থায় পাগলের মত পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তবে শুধু সে একা নয়, তার সঙ্গে ৫৪ জন সঙ্গীও ছিল। যশের নিজেরও প্রতিপত্তি নেহাত কম নয়। যশ বুদ্ধের কাছে এসে কান্নাকাটি জুড়ে দিল, “হায় হায়, দেখুন দেখি কি বিপদ!” বুদ্ধ তাকে শান্ত করলেন, সাদা কাপড় যেমন রঙ শুষে নেয়, বুদ্ধের কাছ থেকে সেইরকম যশ শুষে নিল জ্ঞান, যে, যে বা যা জাত হয়েছে, তার মৃত্যুও অবশ্যম্ভাবী। বুদ্ধ তাকে শিষ্যত্বে বরণ করে নিয়ে নির্বাণের পথ প্রদর্শন করলেন। যশকে ভিক্ষু হতে দেখে বাকী ৫৪ জন সঙ্গীও সংঘে যোগ দিল।
তৃতীয় অধ্যায়
আলোকিত জন তখন এই ৬০ জন শিষ্যকে মহাধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দিকে পাঠিয়ে দিলেন।
“যাও তোমরা, যে পথে মানুষের মঙ্গল ও আনন্দ বিধান হবে, তার উদ্দেশ্যে রওনা দাও ।”
“যাও, যে পথে সর্বমানবের কল্যাণ ও জগতের প্রতি করুণা বিকশিত হবে, সে পথে এগিয়ে চল ।”
“তোমরা জোড়ায় জোড়ায় যাও, কিন্তু যে যার মত কাজ কর। এবার তবে এগিয়ে যাও,মানুষকে উদ্ধার কর, মানুষকে সংঘে গ্রহণ কর।
“মানুষকে সদ্ধর্ম চিনতে সাহায্য কর; কামনা বাসনার ধুলি-মলিনতায় নিমজ্জিত হয়ে যে মানুষ অন্ধ হয়ে আছে, তাকে পুণ্য জীবনের আলো দেখাও। “তারা জ্ঞানের অভাবে মরতে বসেছে। তাদেরকে ধর্ম শেখাও।”
এইভাবে শিশুসুলভ একাকীত্বে, অমিত প্রাণশক্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে তারা ধর্মোপ্রচারে বেরিয়ে পড়ল। ফুলে ফুলে রক্তরাগে রঞ্জিত শাখাপ্রশাখা, আশায় আশায় প্রহর হল দীর্ঘ। যে পরম সত্যকে চিরকাল চিন্তাভাবনা করে এসেছে, আজ তাকে মুখ ফুটে বলতে পারছে; এতদিন বুদ্ধের মতন কেউ ছিলেন না যিনি এমন নিশ্চিত সহজ করে বুঝিয়ে দিতেন। তারা যা এতদিন ধরে চিন্তাভাবনা, কল্পনা করে এসেছে, তার সত্য এবার উপলব্ধি হয়েছে, যেন কতদিনের স্বপ্ন পূরণ হল। সংঘের পুষ্প প্রস্ফুটিত হল, ভারত থেকে বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ল।
“সৎ সুগন্ধ দূর দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ল” ।
এই সময় বুদ্ধের কাছে একজন এসে জানতে চাইলেন, গৃহস্থ অবস্থায় বাড়িতে থেকে এ ধর্ম পালন করা সম্ভব কিনা। বুদ্ধ বললেন, “সাধুও যা, গৃহস্থও তাই, যে অবস্থায় উভয়েই “আত্ম” বোধ বিসর্জন দিয়ে সমস্ত প্রাণীর প্রতি সমদৃষ্টি প্রদান করেন, তাঁরা উভয়েই সমান।” কয়েকদিনের মধ্যেই বুদ্ধের প্রায় সহস্র নুতন শিষ্যলাভ হল। তিন কাশ্যপ ভ্রাতৃত্রয় আর তাঁদের সমস্ত শিষ্যগণ বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। এঁরা সকলে অগ্নি-উপাসক। গয়ার কাছে হস্তিশিলা (elephant rock) নামে এক পাহাড় ছিল। সেই পাহাড় থেকে দেখা যায় সুমুখে রাজগৃহের বিস্তীর্ণ ছড়ানো উপত্যকা ।
দূর-দিগন্তে হঠাৎ করে দাবানল জ্বলে উঠেছে। তা দেখে বুদ্ধদেব সেই সহস্র অগ্নি-উপাসকদের কাছে তাঁর আদিত্য পরিযায় সূত্র ব্যাখ্যা করলেন। “হে সাধুগণ, সর্বত্র আগুন লেগেছে, তাকিয়ে দেখুন। কিন্তু আগুন কোথায় লেগেছে? “চক্ষু, হে সাধুগণ, চক্ষুতে অগ্নিসংযোগ হয়েছে; অবয়বে অগ্নিসংযোগ হয়েছে, নয়ন-চেতনায় আগুন লেগেছে, চোখ যা দেখে তার সবকিছুতে আগুন লেগেছে, তাবৎ বোধ, সংবেদনা, সে সুখের কি দুঃখের, কি সুখদুঃখ রহিত, আগুন হতে সঞ্জাত, তাতেও আগুন লেগেছে।
এ আগুন কিসের আগুন? এ আগুন লালসার আগুন, ঘৃণার আগুন, রিরংসার আগুন, জন্ম, জরার, মৃত্যুর, দুঃখের, শোকের, হতাশার আগুন। কর্ণে অগ্নি সংযোগ হয়েছে, শব্দেরা সব অগ্নিদগ্ধ, নাসিকায় অগ্নি, অগ্নিদগ্ধ ঘ্রাণ, জিহ্বায় আগুন, স্বাদ পুড়ে যাচ্ছে, শরীরে আগুন, যা কিছু স্পর্শ করা যায় তার সবেতে আগুন, মস্তিষক্কে আগুন, ধারণায় আগুন, মনসিজ-চেতনায় আগুন, তাবৎ বোধ, সংবেদনা, সে সুখের কি দুঃখের, কি সুখদুঃখ রহিত, আগুন হতে সঞ্জাত, তাতেও আগুন লেগেছে।
“সাধুগণ, এই সব দেখে যাঁরা প্রাজ্ঞ, তাঁদের চোখ সম্বন্ধে ঔদাসীন্য জন্মায়, অবয়ব সম্বন্ধে ঔদাসীন্য জন্মায়, নয়ন চেতনা সম্বন্ধে তাঁরা উদাসীন হন, তাবৎ বোধ, সংবেদনা, সে সুখের কি দুঃখের, কি সুখদুঃখ রহিত, আগুন হতে সঞ্জাত সমস্ত কিছতেই তাঁরা উদাসীন। শ্রবণেন্দ্রিয় সম্বন্ধে তাঁরা উদাসীন, শব্দবোধ নিয়ে উদাসীন, নাসিকা, ঘ্রাণ, জিহ্বা, স্বাদ, শরীর, স্পর্শজাত তাবৎ বিষয়ে উদাসীন, মস্তিষ্ক, ধারণা, মন-চেতনা, যা কিছু বোধ, চেতনা, সমস্ত বিষয়ে তাঁরা উদাসীন।
“এই ঔদাসীন্য যখন উপলব্ধি হয়, তখন তাঁরা আসক্তি রহিত হন, তখন তাঁরা মুক্ত । “যখন মুক্তি আসে, তখন উপলব্ধি করেন যে মুক্ত হয়েছেন।
“তখন বোধ জন্মে যে পুনর্জন্মের অন্ত হয়েছে, বোঝেন যে পুণ্য জীবন প্রাপ্ত হয়েছেন, যা করা উচিৎ তাই করেছেন, ইহজগতের তিনি কেউ নন। এই-ই পরম সত্য!”
অজস্র শিষ্যসমেত পরম শ্রদ্ধেয় জন এবার মগধের রাজধানী রাজগৃহে অবতীর্ণ হলেন।
সেখানে বুদ্ধদেব একটি শান্তস্নিগ্ধ কাননে অবস্থান করছেন, এমন সময় মহারাজ বিম্বিসার তাঁর পাত্র, মিত্র, অমাত্য, সৈন্যাধ্যক্ষ, ব্রাহ্মণ, পুরোহিত পার্ষদ সহ দেখা করতে এলেন। মহারাজ বিম্বিসার এককালে শাক্য রাজপুত্রের প্রাসাদ ত্যাগ করা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন, তারপরে সিদ্ধার্থকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়েছিলেন যে কোনদিন যদি তিনি সর্বোচ্চ বোধি প্রাপ্ত হন, তাহলে রাজগৃহে প্রত্যাবর্তন করবেন।
পরম শ্রদ্ধেয় জনের সঙ্গে উরুবিল্ব কাশ্যপ কে একসঙ্গে দেখে মহারাজ ও তাঁর সঙ্গীরা মনে মনে ভাবলেন ব্যাপারটা কি? এদিকে মহারাজ বিম্বিসার ও অন্যান্য রাজন্যবর্গের সামনে উরুবিল্ব কাশ্যপ পরমজনের প্রতি সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করে ব্যাপার কি তা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিলেন। বুদ্ধের চরণে প্রণিপাত করে কাশ্যপ ব্যখ্যা করে বললেন যে নির্বাণের পরম শান্তি উপলব্ধি করার পর তাঁর আর যাগযজ্ঞ, বলিদান ভাল লাগে না,
“ওতে নারীসঙ্গ আর ভোগবিলাসের চেয়ে উচ্চতর কিছু পারিতোষিকের আশা নেই” প্রাচীন মহাকবির ভাষা ধার করে বলতে হয়। এই পুরনো-পন্থী সাধুরা যখন উপলব্ধি করলেন যে মৃত্যুর কারণ জন্ম, আবার জন্মের কারণ লোভ লালসা কৃত কর্ম, তাঁদের কাছে প্রতীত হল বুদ্ধদেব যেন কোন এক নদীর তীরে দাঁড়িয়ে আছেন, আর সেই নদী দিয়ে মানুষ জলে ভেসে যাচ্ছে, আর বুদ্ধদেব জলে ভেসে যাওয়া মানুষদের ডেকে বলছেন, “ভো! ওঠো জাগো! জলে ভেসে যেতে যেতে স্বপ্নের নদী তোমার কাছে পরম প্রিয় মনে হতে পারে, কিন্তু এই বয়ে চলা স্রোতের তলায় রয়েছে কুমীরে আকীর্ণ খরস্রোতা এক সরোবর। জেনে রেখো যে এই নদী দুরভিসন্ধি, এই সরোবর কামুক লালসাপূরর্ণ ভোগবাদী জীবন, সেখানে ক্রোধের তরঙ্গ, খরস্রোত লালসা, আর কুমীর নারীসম্ভোগ।”
মানবচরিত্র দেখে আর ধর্ম শিক্ষা দিতে গিয়ে বুদ্ধদেব বুঝেছিলেন যে, এই যে রাজা ও পাত্রমিত্র রা তাঁর কাছে এসেছেন এঁদের হয়ত কিছু উদ্দেশ্য আছে। এঁরা অহঙ্কারী, বিত্তবান, প্রতিপত্তিশালী, তথাপি এসেছেন এই আশায় যে বুদ্ধের শিক্ষাতে তাঁদের কি লাভ হবে তা যাচাই করতে, কারণ বুদ্ধদেবের শিক্ষা নিয়ে এঁদের মনে সংশয় আছে । বুদ্ধদেব সম্যক দিব্যজ্ঞানী । তাই তিনি তাদের শিক্ষা দিলেন যে কি দারিদ্র, কি প্রাচুর্য, কি জ্ঞান, কি অজ্ঞানতা, বেঁচে থাকা, না থাকা, কোনকিছুতেই ব্যক্তিমানুষের কিছু আসে যায় না। তিনি তাদের বোঝালেন, মানুষ সত্যি বলতে কি, নানান সমষ্টির একটা পিণ্ড বই কিছু নয় ।
“একটা হাড়ের মজবুত খাঁচা তৈরী করা হল, তাকে রক্তমাংস দিয়ে ঢাকা দেওয়া হল, তারপর সেখানে জরা, মৃত্যু,বার্ধক্য, অহংকার, আর প্রবঞ্চনার আস্তানা গড়ে উঠল।
“এই সাজানো গোছানো জুড়ে দেওয়া মাংসপিণ্ডটার দিকে তাকিয়ে দেখুন, সেখানে শুধুই ক্ষতের প্রলেপ, তার নিজস্ব কোন শক্তি নেই, কোন কিছু আঁকড়ে থাকা নেই।
“ ‘অহংবোধের জায়গাই নেই কোথাও, জন্ম-মৃত্যু দুঃখ সঞ্জাত পিণ্ডটাকে, যাকে শরীরের অংশ বলে মনে করছি, এ শরীর কিন্তু আমি নই, শরীরে আমিত্বের কোন স্থান নেই, দিনের শেষে আছে শুধু পরম অনন্ত এক শান্তি। আর কিছু নেই।
“অহংবোধের চিন্তাই যাবতীয় দুঃখের উৎপত্তির কারণ, পৃথিবীর সঙ্গে একসূত্রে গ্রথিত, কিন্তু যখনই এই বোধ জন্মায় যে কোন “আমি” কে আর বাঁধা যাবে না, তখন যাবতীয় বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়। কোথাও কোন বন্ধন নেই, এই উপলব্ধিমাত্রই মুক্তির বোধ হয় । সত্যি বলতে কি, “আমি” কোথাও নেই। “না কর্মী, না জ্ঞানী, না প্রভু, না দেবতা, কেউ নেই কোথাও, তবু, এতৎসত্ত্বেও, জন্মও আছে, মৃত্যুও আছে, যেমন প্রতিদিন প্রভাত হয়, রাত নামে, ক্রমাগত চলতেই থাকে ।
“এবার যা বলি শুনুন। ষড়েন্দ্রিয় আর ছয়টি বস্তুকে সংযুক্ত করলে ছ রকমের চেতনার উদয় হয়। চোখ আর দৃশ্যের মিলনে দৃষ্টির চেতনা; কান আর শব্দের মিলনে শব্দের চেতনা,; জিহ্বা আর আস্বাদের মিলনে স্বাদের চেতনা; নাসিকা আর ঘ্রাণের মিলনে আঘ্রাণের চেতনা; শরীর আর স্পর্শের মিলনে স্পর্শের চেতনা; মস্তিষ্ক আর চিন্তার মিলনে চিন্তার চেতনা; তারপর স্মৃতি।
“আতস কাঁচ রৌদ্রজ্জ্বল দিবা দ্বিপ্রহরে শুকনো কাঠের ওপরে ধরলে সেখানে যেমন আগুনের আবির্ভাব হয়, তেমনি, বহিরিন্দ্রিয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর মিলনে চেতনার জন্ম হয়, অহং, যা কিনা চেতনার জনক, তার জন্মও এইখানেই।
“বীজ থেকে অঙ্কুরোদ্গম হয়, তবু বীজ অঙ্কুর নয়, অথচ অঙ্কুর থেকে সে ভিন্ন কিছুও নয়। এই হল তাবৎ জীবের জন্মরহস্য।”
বোধ আর স্মৃতি সঞ্জাত অহং অনিত্য, কাজেই এর লয়ও অনিবার্য, এই জ্ঞান উপলব্ধি করার পর মহারাজ বিম্বিসার ও তাঁর সমস্ত অমাত্যগণ বুদ্ধ, ধর্ম, ও সংঘ — গার্হস্থ্যে এই ত্রিরত্নে শরণ নিলেন। মহারাজ বিম্বিসার তখন পরম শ্রদ্ধেয়জন ও তাঁর সমস্ত শিষ্যদের রাজপ্রাসাদে আমন্ত্রণ জানালেন, ও সংঘকে তাঁর নিজের প্রমোদকানন, যার নাম বেলুবন, উপহার দিলেন।
বেলুবনে মহাগুরু ও তাঁর গৃহত্যাগী শিষ্যদের থাকার বন্দোবস্ত হল। বুদ্ধদের ও তাঁর শিষ্যদের শরীর পরিচর্যা ও চিকিৎসার জন্য মহারাজ বিম্বিসার তখনকার দিনের বিখ্যাত চিকিৎসক জীবককে নিযুক্ত করলেন । জীবকের নির্দেশেই ভিক্ষুরা, যাঁরা এতদিন চীর ও কাষায় পরিধান করে দিন কাটাতেন, তাঁরা সাধারণ মানুষের কাছ থেকে হলুদ-রঞ্জিত বস্ত্র গ্রহণ করে পরিধান শুরু করলেন।
বেলুবন নামে জায়গাটি শহরের উপকন্ঠে, সেখানে নানারকমের তোরণ, খোলামেলা হাঁটার জায়গা, বাগান রয়েছে। জায়গাটি দিনের বেলায় যেমন শান্ত, আবার রাত হলেই নিগূঢ় নীরব, জনস্থান থেকে বহুদূরে, তাই একান্তে বসবাস করার কি মনসংযোগ করার জন্য আদর্শ।
সেখানে বাগান, আশ্রম, ধ্যানগৃহ কুটীর, চারপাশ পদ্মদীঘি দিয়ে ঘেরা, সেখানে আম গাছের মিষ্টি গন্ধ ম’ম’ করে, সরু দীর্ঘ গগনচুম্বী তালগাছের সারি, তালগাছের ভিজে পাতা যেন ছাতার তলায় সন্ন্যাসীদের মনে করিয়ে দেয় তালের বীজ, যেন জাগতিক সুখ, সুখী জীবনের সমতাকে বিপর্যস্ত করে আকাশে উঁকি দিচ্ছে ।
চতুর্থ অধ্যায়
একদিন অশ্বজিৎ নামে বুদ্ধদেবের প্রথম পাঁচ শিষ্যের একজন, রাজগৃহে মাধুকরী করছিলেন, এমন সময় সাধু সারিপুত্রের সঙ্গে দেখা। অশ্বজিতের আনন্দময় আভিজাত্যপূর্ণ চেহারা দেখে অবাক হয়ে সারিপুত্র শুধোলেন, “কে আপনার গুরু? তিনি কোন সম্প্রদায়ের?” সারিপুত্রের মৌদগল্যায়ন নামে এক সতীর্থ ছিলেন । বহুদিন আগে তাঁরা দুজনে স্থির করেছিলেন যে দুজনের মধ্যে যিনি প্রথম পরম সত্য ও অমৃতের সন্ধান পাবেন, তিনি অন্যজনকেও জানাবেন। অশ্বজিৎ বললেন, “শাক্যবংশজাত গৃহত্যাগী এক মহৎ সাধু আছেন, তিনি আমার গুরু, আমি তাঁরই শিষ্য”, এই বলে গেয়ে উঠলেন,
“যা কিছু কারণ হতে উথ্থিত হয়, বুদ্ধ বলেছেন তার কারণ সমুদায়, কিসে তার লয়, পরম জন সে কথাও বলেছেন”
এমন কথা শোনামাত্র সারিপুত্র উপলব্ধি করলেন তিনি অমৃতের সন্ধান পেয়েছেন। মৌদগল্যায়নের কাছে গিয়ে যা শুনেছেন তা বললেন । সারিপুত্র ও মৌদগল্যায়ণ দুজনে সশিষ্য তথাগতের কাছে গেলেন।
সারিপুত্ত ও মৌদগল্যায়ণকে আসতে দেখে আলোকিত জন তাঁর শিষ্যদের বললেন, “এই যে দুজন আসছেন, কালক্রমে এঁরাই আমার সবচেয়ে বিখ্যাত দুই শিষ্য হবেন, একজন জ্ঞানে অতুলনীয় (মৌদগল্যায়ণ) আর অপরজন অলৌকিক ক্রিয়াকর্মের কারণে বিখ্যাত হবেন (সারিপুত্র)! স্বাগতম!”
এই দুই সাধু পরবর্তীকালে পবিত্র ধর্মগ্রন্থের বিভিন্ন পর্ব লিখেছিলেন। তাঁরা সশিষ্য সংঘে যোগ দিলেন ।
মহাকশ্যপ এক ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ। তার ওপর তিনি মানবহিতৈষী ও জ্ঞানী, তাঁর খ্যাতি দেশজোড়া । তিনি সেই সময়ে সদ্য তাঁর স্ত্রী, তাঁর বিপুল ঐশ্বর্য, অট্টালিকা, এ সমস্ত কিছু ত্যাগ করে মুক্তির পথ সন্ধান করছেন। যশ নামে সেই উন্মত্ত যুবকের মতই তাঁর অবস্থা। ঘুরতে ঘুরতে একদিন মধ্যরাতে বুদ্ধের শিবিরে এসে হাজির।
“আপনি পরম ধর্মের আনন্দ উপভোগ করেছেন, বিনম্রভাবে আপনি শুদ্ধচিত্তের প্রার্থনা করেছেন, আপনি নিদ্রাজয়ী, ও এখানে শ্রদ্ধাসহ আমার কাছে এসেছেন”, দয়ার্দ্রচিত্তে বুদ্ধ বললেন, “শুধু আপনার জন্য আমি প্রথম সাক্ষাতে আমার যা করণীয় করব। ঔদার্য ও দানশীলতার কারণে আপনি লোকসমাজে সর্বজনবিদিত, আমার কাছ থেকে সম্যক বিশ্রামের দান গ্রহণ করুন, এবং বিশুদ্ধিতার নিয়মাবলী জেনে নিন।“
পরমজ্ঞানী বুদ্ধদেব মহাকশ্যপ নামে এই ধনবান মানুষটির অকারণ ও অত্যধিক দয়া দাক্ষিণ্যের স্বভাবে কিছুটা রাশ টানতে চাইছিলেন। এঁর সবচেয়ে আগে একটু শান্ত হওয়ার দরকার ছিল। বুদ্ধদেব বললেন, “জগতের এই যে অতিচাঞ্চল্য, মহাব্যস্ততার ভাব, একেই আমি মনে করি সমস্ত দুঃখের মূল।
“জন্ম মৃত্যুর এই ক্রমাগত টানাপোড়েন দেখে আমার মনে হয় আমাদের উচিৎ একটা অপ্রতিরোধী, নিষ্ক্রিয় বিগতস্পৃহ অবস্থা অবলম্বন করা; সম্মতা (সমতা)’র সুউচ্চ লক্ষ্য, মৃত্যুহীন পরম শান্তির স্থান।
“সমস্তই শূন্য! এখানে না অহং, না আমিত্বের কোন স্থান আছে, সমগ্র জগৎ মায়াময়; আমরা একেকজন নানাগুণের সমষ্টিগত আধারবই আর কিছু নই।”
মহাকশ্যপ উপলব্ধি করলেন দয়াদাক্ষিণ্যে অহং-এর কোন জায়গা নেই।
“আপনিই প্রকৃত তত্ব উপলব্ধি করেছেন, আপনার সরল হৃদয় দানধ্যান করতে চায়; কারণ ধনসম্পদ অনিত্য; অন্যের কাছে বিলিয়ে দেওয়াই শ্রেয়;
“যখন ধনদৌলত আগুনে পুড়ে ছারখার হয়ে যায়, যতটুকু বেঁচে থাকে, জ্ঞানীজন সমস্ত কিছু অনিত্য জ্ঞানে অবলীলাক্রমে সেসবও দান করে অবাধে বিতরণ করে দেন, যা জমিয়েছিলেন তাই দিয়ে পরোপকার করেন।
“কিন্তু মূর্খ মানুষ তাদের আঁকড়ে ধরে রাখতে চায়, পাছে হারিয়ে যায় সেই ভয়ে মরে, উদ্বেগে ক্ষয়ে যেতে থাকে দিনের পর দিন, কাল্পনিক কি এক ভয় তাকে তাড়িয়ে বেড়ায়, দুঃস্বপ্ন দেখে সব বুঝি হারিয়ে গেল, সব, এমনকি নিজেও;
“দানশীল মানুষের মনে কোন পরিতাপ নেই, কোন তাড়িয়ে বেড়ানোর ভীতি নেই; উন্মুক্ত পুষ্পের প্রায় তাঁর পুরস্কার, ফুল থেকে ফল জন্মে — কিন্তু ফল কেমন হবে প্রথমেই বুঝতে পারা যায় না। এই বোধ-ই স্থিতধী মানুষের পথ, কোন কিছুর উপর নির্ভর করে নেই ।
“শৃন্বন্তু!
“আমরা অমৃতপথ প্রাপ্ত হলেও ক্রমাগত দয়াশীল কাজের মাধ্যমে আমরা নিজেদের পরিপূর্ণ করি; অন্যত্র আমরা যে দয়া, করুণার প্রদর্শণ করি, তার পরিণামেই আমাদের পরিপূর্ণতা প্রাপ্তি।
“অতএব! দানশীল মানুষ পরমাগতির সন্ধান পেয়েছেন; যিনি বৃক্ষের চারা রোপণ করেন, তিনি শীতল ছায়ার বিশ্রাম পান; পুষ্প চয়ন করে, গাছ যখন পরিপূর্ণ হয়, সেখান থেকে ফল লাভ করেন, দানের ফলও তেমনই — তাতে আনন্দ ও পরম নির্বাণ!
“খাদ্য বিতরণ করে আমরা শক্তি সঞ্চয় করি; বস্ত্র বিতরণ করে নিজেদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করি; ধর্মশালা স্থাপন করে সর্বোচ্চ দানের সুফল লাভ করি, নিজের স্বার্থসিদ্ধি বা কতটা লাভ করলাম না ভেবেই করি; তাই এতে পরম চিত্ত শান্তি!
বুদ্ধদেবের এই শিক্ষা পরবর্তীকালে দান পারমিতা বলে লিখিত হয়েছিল। দানপরায়ণতা, ছটি গুণের অন্যতম, অষ্টাঙ্গমার্গের শেষ ছ’টি সোপানের একটি: দান, শীল, ক্ষন্তি (ধৈর্য), বীর্য, ধ্যান, প্রজ্ঞা। মহাকশ্যপ এই শিক্ষা গ্রহণ করে দীক্ষিত হলেন, ও গেয়ে উঠলেন,
“এতদিনের ভারি বোঝা নামিয়ে রাখলাম,
পুনর্জন্মের কারণ আর আমার নেই,
কখনো ভাত কাপড়ের কথা ভাবি নি,
কখনো ভাবি নি মানসিক বিশ্রামের,
আমাদের গৌতম অনবধনেয়,
তাঁর গ্রীবায় চতুষ্কোণ তোরণ,
সেখানে বিরাজ করে একাগ্রতা; হ্যাঁ, সেই মহর্ষি,
যাঁর হাতে আছে নির্ভরতা আর বিশ্বাস,
তাঁর সুউচ্চ ললাটে অন্তর্দৃষ্টি,
মহৎ জ্ঞানীজন
শান্ত পদক্ষেপে পরমশান্তিতে তিনি সদা সঞ্চরমান”
বুদ্ধের মহাপ্রয়াণের পর, মহাকশ্যপ বৌদ্ধসংঘের প্রথম মহাগুরু হয়েছিলেন, ও ত্রিপিটক একত্রিত করেছিলেন; এই কাজ যদি তিনি না করে যেতেন, মহৎ জনের বাণী আজ ২৫০০ বছর পরে আমাদের কাছে পৌঁছত না। তবে জাগ্রত জন, বুদ্ধের, মানসচেতনায় ২৫০০ বছর পদ্মপত্রে বারিবিন্দুসম। ধর্মের সারণী অনন্ত, নিরবিচ্ছিন্ন। মহাবিশ্বের সর্বদিকে বুদ্ধগণ সদাবিরাজমান; গঙ্গাতীরের অযুত বালুকারাশির ন্যায়। এঁরা সতত বিশ্বের মঙ্গল-কামনায় তূরীয় বোধির জ্ঞানালোক বিতরণ করে চলেছেন। এখন আমিও সকল প্রাণীর মঙ্গলকামনায় অযুতসহস্রদিকে বুদ্ধালোক বিতরণ করে চলেছি; নানাপ্রকার প্রাণীর প্রতি আমি ধর্মের প্রকাশ করে চলেছি। যার যার ধারণ ক্ষমতামত আমি সতত বিভিন্ন ভাবে ধর্মের বিকাশ করি; তাই বুদ্ধের, বিশ্বগুরুর প্রহেলিকা অবধান করার চেষ্টা করি। সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্ব পরিত্যাজ্য; তোমরা সকলে বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হবে।”
মহাকশ্যপের দীক্ষান্তে শাক্যমুনি গৌতম ধরণীর পথ বেয়ে তাঁর জন্মস্থান, মহারাজ শুদ্ধোদনের রাজ্য গোরক্ষপুরে এলেন। মহাগজের দুর্জ্ঞেয় একাকীত্বে, বহু শিষ্যসহ ধীরপদে বুদ্ধদেব কপিলাবস্তুর কয়েক ক্রোশের মধ্যে এসে উপস্থিত হলেন। সেখানে তাঁর কৈশোরের সুরম্য প্রাসাদ তখন, মায়াময়, আলোকিত মুকুরের অটল মহিমায় স্থির; যেন শিশুদের রূপকথার ছেলেভুলনো হর্ম্যতোরণ। তাঁর আগমনের সংবাদ পেয়ে মহারাজ শুদ্ধোদন ত্রস্তপদে সত্বর এলেন।
বুদ্ধকে দেখে বড় দুঃখে বললেন, “এইতো আমি আমার পুত্রের দর্শন পেলাম; সে আগের মতই আছে, কিন্তু তার পুরনো হৃদয় যেন আর তার মধ্যে নেই, নেই সেই পুরনো আত্মার উষ্ণতার লেশমাত্র, সে যে শূন্য, শীতল।” যেন কতদিনের পুরনো সখার কথা ভাবছেন, এইভাবে পিতাপুত্র পরস্পর পরস্পরের দিকে চেয়ে রইলেন।
বুদ্ধ: “আমি জানি যে মহারাজের হৃদয় স্মৃতিমেদুর ভালবাসায় পূর্ণ, এও জানি যে পুত্রহেতু তিনি দুঃখের পর দুঃখ বরণ করেছেন, কিন্তু এখন! পুত্রপ্রেমের, পুত্রের কথা চিন্তায় যে বন্ধনে তিনি আবদ্ধ, সে বন্ধন ছিন্ন হোক!
“স্তব্ধ হোক প্রেমময় চিন্তাভাবনা, আপনার শান্ত মন, আমার, আপনার পুত্রের কাছ থেকে গ্রহণ করুক ধর্মের পরিপোষণ, যে পরিপোষণ অদ্যাবধি কোন পুত্র তার পিতাকে দিতে পারে নি, সেই পরিপোষণ; হে রাজন, হে আমার পিতৃদেব, আমি আপনাকে সেই পরিপোষণ নিবেদন করি!”
“যে অমর অপার সিদ্ধি আপনার প্রতি নিবেদন করি মহারাজ, সেখানে কর্মের উপচিতিতে জন্মের উন্মেষ; কর্মের ফলগেতু প্রায়শ্চিত্ত; অতএব রথচক্র যেমন বৃষের পথ অনুসরণ করে চলে, কর্ম তেমন ফল বয়ে আনে, সকল কার্য উদ্ধারে আপনি কতই না যত্নবান! আপনি কতই না তৎপর যে জগতে আপনার কার্য যেন কেবল সকলের মঙ্গলার্থে সাধিত হয়।
“তবে শুধু এক ঐশ্বরিক পুনর্জন্মের কামনায় যেন সৎকার্য না করেন মহারাজ! দিবারাত্র অমঙ্গল চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে, সর্বজীবের প্রতি প্রেম ও সমদৃষ্টিপাত করে, আপনি যেন মনের যাবতীয় কলুষতা থেকে মুক্ত হয়ে নীরব ধ্যানমগ্ন হতে পারেন; এতেই সকলের মঙ্গল, এ ব্যতীত আর কোন সত্য নেই।
“মনে রাখবেন স্বর্গ, মর্ত্য পাতাল সবই সমুদ্রের ফেনা বই আর কিছু নয়।
“নির্বাণ! এতেই সর্বোত্তম, পরম, শান্তি!
“স্থিতচেতনা, সকল প্রমোদের শ্রেষ্ঠ প্রমোদ!
“জ্ঞানীজন অনন্ত শান্তির মাঝে আপন নিবাস খুঁজে পান। সেখানে যুদ্ধের, দ্বন্দ্বের স্থান নেই; না অশ্ব, না রথ, না হস্তী, না সৈন্যসামন্ত!
“একযোগে তাবৎ জন্ম, জরা, মৃত্যুতে ছেদ টানুন!
“অজ্ঞানতা, লোলুপতা, ক্রোধের অবসানে পৃথিবীতে জয় করার আর কিইবা বাকী থাকতে পারে!”
পুত্রের কাছ থেকে এমন মমতায় ভীতি জয় করার, জন্মের তমসাচ্ছন্ন যাতনা থেকে উদ্ধার পাবার কথা শুনে, মহারাজ রাজত্ব পরিত্যাগ করে, এমনকি রাজ্য অবধি ত্যাগ করে চেতনার অবগাহনে ডুব দিলেন, অনন্ত মহদ্ধর্মের তোরণ উন্মুক্ত হল তাঁর সামনে! মহারাজ শুদ্ধোদন ধ্যানময় মধুর যেন আস্বাদ পেলেন । রাত্রে অনন্ত আকাশের পানে তাকিয়ে মহারাজ আপন মনে উপলব্ধি করলেন, “আকাশ ভরা এই সূর্য তারার মাঝে কি আনন্দ যে আমিও স্থান পেয়েছি।“, তারপর, “তবু শুধু বেঁচে থাকা তো নয়, নক্ষত্রখচিত এই মহাজগত মহাজগত মাত্র নয়!”, তখন বুদ্ধের শেখানো সকল চেনার মাঝে সকল অচেনার উপলব্ধি হল তাঁর।
পঞ্চম অধ্যায়
পুত্র রাহুলকে তাঁর পথে নিয়ে আসবেন এই মনোকামনায়, মৌদগল্যায়নকে সঙ্গে নিয়ে, পরমজন, জীবনে যাঁকে স্ত্রীরূপে পেয়েছিলেন, সেই যুবরাণী যশোধরার সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। রাহুলের তখন ১৯ বছর বয়স। যশোধরা রাহুলের উত্তরাধিকারের কথা বিবেচনা করে বুদ্ধদেবের কাছে কাতর অনুনয় করলেন।
বুদ্ধদেব বললেন, “আমি রাহুলকে আরো উত্তম উত্তরাধিকার প্রদান করব”, এই বলে মৌদগল্যায়ণকে নির্দেশ করলেন, রাহুলের মস্তক মুণ্ডন করিয়ে সংঘে যোগদান করাতে।
এর পর তাঁরা কপিলাবস্তু থেকে বেরিয়ে পড়লেন। কপিলাবস্তুর কাছে প্রমোদকাননে একদল শাক্য রাজকুমারের সঙ্গে দেখা, এঁরা সকলেই গৌতমের নানান সম্পর্কিত ভাই। এঁদের মধ্যে ছিলেন আনন্দ ও দেবদত্ত — কালক্রমে এঁরা বুদ্ধের পরম মিত্র ও চরম শত্রু রূপে পরিগণিত হবেন। কয়েক বছর পরে পরমজন আনন্দকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে আনন্দ তখন বুদ্ধের মধ্যে কি এমন দেখেছিলেন যে জাগতিক যাবতীয় আনন্দ সম্ভোগ-বাসনা তুচ্ছ করে স্ব-আলোকিত মনের সারাৎসার উপলব্ধিই তখন বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল, তা শুনে আনন্দ বলেছিলেন, “হে, প্রভু! সর্বাগ্রে আমি আমার প্রভুর ব্যক্তিত্বে ৩২টি পরম মহামহিম চিহ্ন দেখেছিলাম। নরম, সূক্ষ্ম, ও স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ হয়ে তারা আমার চোখে প্রতিভাত হয়েছিল।” জ্ঞানের দিক থেকে এই উষ্ণহৃদয় যুবকটির স্থান মৌদগল্যায়ণের পরেই। আবার গুরুর প্রতি একপেশে অন্ধপ্রেম, ও তীক্ষ্ণধীর অধিকারী হওয়াই আনন্দের সংস্কারমুক্ত সমানতা ও সম্যক বোধিপ্রাপ্তির অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। খুব সামান্য ভিক্ষুরাও যে বোধি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে খুব প্রাচীনপন্থী, ভবঘুরে ভিক্ষুদের নাম করা যায়, যেমন সুনীতা (মেথর ছিলেন), অলাবক — যিনি বোধিপ্রাপ্তির প্রাককালে অটবীতে এককালে নরখাদক ছিলেন, ব্যায়ামবীর উগ্রসেন, প্রভৃতি। আনন্দ কালক্রমে বুদ্ধের ছায়া নামে প্রসিদ্ধি পেয়েছিলেন, সদাসর্বদা পরমজনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলতেন; যখন যেখানে যেভাবে বুদ্ধদেব চলতেন, বসতেন, তাঁর পায়ে পায়ে, আনন্দ প্রতিপদে তাঁকে অনুসরণ করতেন। অল্পকাল পরে আনন্দ প্রায় স্বভাবত বুদ্ধদেবের যাবতীয় দেখভালের দায়িত্ব নিয়েছিলেন, বুদ্ধের আসন তৈরী করে রাখতেন, যে শহরে বুদ্ধ যেতেন সেখানে আগে থেকে গিয়ে যাবতীয় ব্যবস্থাপনা করে আসতেন, বুদ্ধদেবের যখন যা প্রয়োজন হত, আনন্দ সেই প্রয়োজন মেটাতে তৎপর থাকতেন। আনন্দ বুদ্ধদেবের সর্বক্ষণের সঙ্গী, বুদ্ধদেবও নীরবে সেই সঙ্গ গ্রহণ করেছিলেন।
এর বিপরীত দেবদত্ত। সে নির্বোধ ও হিংসুটে। দেবদত্ত সংঘে যোগ দিয়েছিল অতীন্দ্রিয় সমাপত্তি অর্জনের উদ্দেশ্য নিয়ে; এই অতীন্দ্রিয় সমাপত্তি গভীর ধ্যান অতিক্রম করার পরের চেতনার স্তর — যাতে করে দেবদত্ত কিছুটা জাদুমন্ত্র আয়ত্ত করতে পারে। তাতে এই জাদুমন্ত্র যদি বুদ্ধের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে হয়, তাই সই। দেবদত্ত নিজের একটা আলাদা সম্প্রদায় গড়ববার ছক কষেছিল।
সমাপত্তির যে ঐশ্বরিক চেতনা, তার মধ্যে ছিল অতীন্দ্রিয় ভাবসংযোগ, অতীন্দ্রিয় উপায়ে মানুষের মনের কথা বুঝে নেওয়া। গোরক্ষপুরে যখন বুদ্ধদেবের সঙ্গে প্রমোদকাননে দেবদত্তের প্রথম দেখা হয়, তখন তার এই দুরভিসন্ধির কথা বোঝা যায়নি। বুদ্ধ সর্বজীবের প্রতি সমপ্রেমসম্পন্ন, সর্ব জীবে একই শূন্যতা দর্শন, দীক্ষার সময়ে দেবদত্ত তার মনে কি পুষে রেখেছে, তা নিয়ে বুদ্ধের খুব একটা কিছু যেত আসত না। এমনকি পরেও, দেবদত্ত যখন বুদ্ধকে মারবার চেষ্টা করছেন, তখনো, আমরা পরের দিকে দেখব, যে, পরমজন অপরিমিত মাধুরীতে তাকে অন্তর থেকে ক্ষমা করে আশীর্বাদ করেছেন।
মহাগুরু সশিষ্য রাজগৃহে গেলেন, সেখানে সুদত্ত নামে এক ধনী বণিক তাঁদের সম্বর্ধনা জানালেন। সুদত্ত গরীব ও অনাথ মানুষের প্রতি তাঁর দয়াদাক্ষিণ্যের কারণে অনাথপিণ্ডক নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। এক রাজকুমারের কাছ থেকে প্রচুর অর্থের বিনিময়ে তিনি জেতবন নামে একটি উদ্যান কিনে নিয়েছিলেন। সেখানে বুদ্ধদেব ও তাঁর শিষ্যদের জন্য চমৎকার একটি মঠ তৈরী কে দিয়েছিলেন। সেই মঠটিতে প্রায় ৮০টা প্রকোষ্ঠ, বাড়িঘর, বারান্দা, স্নানের জায়গা ছিল। শ্রাবস্তীনগরীর অদূরেই, এখানেই পরমজন অনাথপিণ্ডকের আতিথ্য গ্রহণ করে বসবাস শুরু করলেন। শুধু বর্ষাকালে রাজগৃহের বেলুবনের মঠে চলে আসতেন।
সেইখানে অধিকাংশ সময়ে তিনি একাকী অরণ্যে সময় কাটাতেন। অন্যান্য সাধুরা যে যার নিজের মতন করে সাধনা করতেন, ধ্যান করতেন, অরণ্য থেকে উদ্গীত প্রেমময় নীরবতা যেন পান করতেন তাঁরা। সেই অরণ্যে বুদ্ধদেব শান্ত সমাহিত হয়ে গাছের ছায়ায় কুশাসনে বসে থাকতেন। সে জীবন কখনো সুখকর (“জঙ্গলটি ভারি রমণীয়; যে জায়গায় জগতের কোন আনন্দ নেই, সেখানে নির্লিপ্ত উদাসীন মানুষ আনন্দ অনুভব করে, কারণ তারা তো ভোগবাসনার সন্ধানে ফেরে না”); সবসময় অবশ্য সুখকর ছিল না।
“শীতের রাত বড় শীতল প্রভু”, সাধুরা গান ধরতেন, “হিমকাল সমাসন্ন, গোচারণ হেতু রুক্ষ্ম জমি; পত্রের এই পালঙ্কটি নেহাতই শীর্ণ, কাষায বস্ত্র বড়ই ক্ষীণ; শীতের হাওয়া অন্তহীন”।
তবে সনাতন ভারতের সন্ন্যাসীদের প্রথানুযায়ী এই সব সাধকের দল দিব্যজ্ঞানলাভ করেছিলেন, তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন যে ইহজগতে মশামাছির কামড়, সর্পের গমন, বৃষ্টিভেজা শীতের রাত, কি গ্রীষ্মের খরতাপ অপেক্ষা নিকৃষ্টতর আরো বহু বিষয় আছে।
বুদ্ধদেব লোভ জয় করেছিলেন, কাম, মোহজাল ছিন্ন করেছিলেন; বুদ্ধ সকলের কাছ থেকে অন্ন গ্রহণ করতেন; সে খাবার খারাপ হোক, ভাল হোক, যা আসত, যার কাছ থেকে আসত, সব তিনি গ্রহণ করতেন। ধনী কি দরিদ্র, উচ্চ কি নীচ, তিনি ভেদাভেদ করতেন না। ভিক্ষাপাত্র পূর্ণ হয়ে গেলে একাকী নির্জনতায় ফিরে আসতেন। সেখানে প্রার্থনা করতেন সর্বজীবের দুঃখ, জন্ম-মৃত্যু, মৃত্যু-পুনর্জন্ম, অজ্ঞান তমসায় লিপ্ত জগতের যুদ্ধের পরিত্রাণ, প্রাণীজগতের হত্যা, পিতার পুত্রকে তাড়না, শিশুর আরেক শিশুকে যাতনা, প্রেমিকের ছলনা, ডাকাতের হাতে সাধারণ মানুষের সর্বস্বহরণ, উন্মত্ত রক্তগৃধু মানুষের আরো রক্তপানের লালসা, সাধারণ মানুষের আত্মকৃত শ্মশানে উন্মত্ত ভ্রমণ, জগতব্যাপী দুঃখ, এক ভয়ংকর পশু যেন কোথা থেকে ভয়ংকর অনন্ত আঁধারে একে একে প্রাণীকে ছুঁড়ে ফেলছে, এমন আঁধার, সেসবের থেকে পরিত্রাণের। যেই অন্ধ জগতের কার্য কারণ হেতু উন্মাদ অজ্ঞতার অবসান হবে, তৎক্ষণাৎ সেই অবসান কল্পে অন-উন্মাদ, অন-অজ্ঞান রূপ প্রতিভাসিত হবে। যেন মনসরোবরে ডুব দিয়ে ভোরের শিশু স্বর্গে প্রবেশ করছে; সেই মন, যা পরম, সৎচিৎ, যেখান থেকে শূন্যতার বিকিরণ, একমেবাদ্বিতীয়ম, তন্মাত্র, সর্বগামী, একশো ভাগ মনসিজ, যার পরে এই স্বপ্নময় আঁধার যেন ছেয়ে আছে, যেখানে এই মায়াময় শরীর ক্ষণমাত্র উদয় হয়েই পুনরায় চিরকালের জন্য বিলীন হয়ে যায়। হাজার হাজার সাধু সন্ন্যাসীর দল জাগ্রতজনকে অনুসরণ করে চললেন, তাঁরই পথে পথ তৈরী করলেন। শরতের শেষ পূর্ণিমা রাতে মুক্ত আকাশের তলায় শত শত সাধুর মাঝে জাগ্রতজন আসন পাতলেন। তারপর জাগ্রতজন সেই নীরব জনতার দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন,
“সাধুগণ, এই যে নিঃশব্দ, নীরবতা, এই সভা, প্রকৃত অর্থে যেন এক অন্তর্বীজ।
“তাই এই ভ্রাতৃসঙ্ঘ এ জগতে মহত্তম, সর্বজনশ্রদ্ধেয়।
“তাই, এই ভ্রাতৃসঙ্ঘ অতুলনীয়।
“তাই, এই ভ্রাতৃসঙ্ঘে মানুষ পিছনে চলতে হলেও যোগদান করতে চাইবেন।
“আমাদের এই সঙ্ঘে এমন অনেক সাধু আছেন, যাঁরা স্বয়ংসম্পূর্ণ, যাঁরা মায়ার অন্ত দর্শন করেছেন, যাঁরা মুক্তিপ্রাপ্ত হয়েছেন, নিজেদের মুক্ত করেছেন”
এই বলে বুদ্ধ তাঁর যে জাগ্রতজন তাঁর পূর্বজ, সর্বকালে সকল বুদ্ধের প্রতি, সর্বজগতের প্রতি তিনি মহাধরণী মন্ত্রের হৃদয় প্রার্থনা করলেন, অন্তহীন জন্ম-মৃত্যুর চক্র হতে মুক্তির প্রার্থনা,
এইরূপ:
“ওং!
যিনি শক্তি ধারণ করে আছেন,
আপনার রত্নহস্ত উত্তোলন করুন,
শূন্যতায় নিয়ে আসুন তাকে
ধ্বংস করুন,
হে পালনকারী,
পালন করুন সর্বজীবকে
হে বিশুদ্ধকারী,
যারা আত্মবদ্ধ তাদের শুদ্ধ করুন,
তারা যেন যাতনাকে জয় করতে পারে
হে সম্পূর্ণ আলোকিতজন,
সর্বজীবকে আলোকিত করুন,
হে পরমজ্ঞানী পরমকৃপালু,
সর্বজীবকে মুক্ত করুন,
তাদের সকলকে বুদ্ধত্ব প্রদান করুন
তথাস্তু!”
ষষ্ঠ অধ্যায়
মানুষের জেগে ওঠার কথা যেমনই লোকমুখে প্রচারিত হতে থাকল, নারীরা তাঁদের কেশ কর্তন করে, কাষায় বস্ত্র পরিধান করে, ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে বুদ্ধের সঙ্গে দেখা করতে এলেন।
বুদ্ধদেব নিষেধ করে বললেন, “দৃঢ় বাঁধ যেমন নদীকে বেঁধে রাখে, সেইরকম আমিও কিছু নিয়মের বন্ধন করেছি, তাকে অতিক্রম করতে পারিনা।” এই নির্ভীক, নিষ্ঠাবান নারীদের মধ্যে রাজকুমারী যশোধরা, বুদ্ধের মায়ের সম্পর্কে বোন প্রজাপতি গোতমী, এঁরাও ছিলেন। তাছাড়া আনন্দ, গোতমীর অনুনয়ে, এমন জেদ ধরে অনুরোধ করতে লাগলেন, যে বুদ্ধদেব শেষ অবধি আর না করতে পারলেন না। এইভাবে ভিক্ষুণীদের সংঘ সৃষ্টি হল। বুদ্ধদেব আদেশ করলেন, “এঁদের ভ্রাতাদের নীচে স্থান দিতে হবে” “তাহলেও”, পরম পুণ্যজন বললেন, “এই যে এঁদের স্থান দেওয়া হল, এতে করে সদ্ধর্ম আর সহস্র বৎসর বাঁচবে না, পাঁচশো বছর তার আয়ু। ধানক্ষেতে ছত্রাক পড়লে যেমন ধানক্ষেতের নাশ হয়, তেমনি, যখন ঘরকন্না ছেড়ে নারীগণ সংঘে যোগদান করবেন, সংঘও দীর্ঘকাল জীবিত থাকবে না।” এ এক অশনি সংকেত, আর তার পাশাপাশি দেবদত্তের উথ্থানের দিনগুলোয় দেবদত্ত সংঘের কিছু ভিক্ষুণীকে ব্যবহার করেছিলেন।
মহারাজ প্রসেনজিৎ, যাঁর রাজত্বে সতত শান্তি বিরাজমান, অথচ মহারাজ নিজে মহারাণীর সঙ্গে বিবাদ বিসম্বাদ করে দ্বিধাবোধে ভুগছিলেন। মহারাজ সেই সময় পরম পূজ্যের কাছ থেকে ধর্ম-অধর্মের কথা শুনতে ইচ্ছা করে, বুদ্ধদেব-সমীপে শ্রদ্ধাবনত হয়ে উপনীত হলেন, প্রণাম করে দক্ষিণ দিকে সসম্ভ্রমে বসলেন। তখন মহারাজ প্রসেনজিৎকে, ধর্মব্যাঘ্র এই কথা বললেন।
“যারা অসৎ কর্মের হেতু নীচকূলে জন্মেছে, তারাও, সচ্চরিত্র মানুষ দেখলে, তাঁর সম্বন্ধে শ্রদ্ধাশীল হয়, আপনার ন্যায় রাজন, যিনি পূর্বজীবনের কর্মফলহেতু এমন যোগ্যতা অর্জন করেছেন, তিনি যখন বুদ্ধের দর্শনলাভ করেন, না জানি আরো কতই না শ্রদ্ধাশীল।
“যে দেশে বুদ্ধদেব অবস্থান করেন না, সে দেশের তুলনায় যে দেশে তিনি অধিষ্ঠিত, সেখানে যে শান্তি-সমৃদ্ধি বিরাজ করবে, তাতে সন্দেহ কি।
“এখন মহারাজের কাছে সংক্ষেপে ধর্মাধর্মের অবতারণা করব।
“প্রেমময় হৃদয় সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। সকল প্রজাকে একমাত্র সন্তানতুল্য জ্ঞান করা; নিজেকে কোন মিথ্যা তত্বে না জড়ানো; রাজকীয় অহমিকা নিয়ে মাথা না ঘামানো; কপট পরামর্শদাতাদের মিথ্যা মিষ্ট বাক্যে না কান দেওয়া।
“কণ্টকশয্যায় শুয়ে নিজেকে কষ্ট দেবারও কিছু নেই; বরং ইহজগতের অসারতাকে গভীর ধ্যানে উপলব্ধি করা; সদাসর্বদা জীবনের চাঞ্চল্যকে স্মরণে রাখা ।
“কাউকে তুচ্ছ করে নিজেকে মহিমান্বিত করা নয়, বরং আপন অন্তরে সজাত আনন্দ অনুভব করা, আরো আনন্দময় জীবনের দিকে ক্রমাগত এগিয়ে চলা;
“শুনুন মহারাজ! আপনি নিজেই আপনার দীপ, নিজেই আপনার শরণ, এ ব্যতীত অন্য শরণ আর কোথাও নেই। প্রতিষ্ঠিত ধর্মই হোক আপনার দীপ, ধর্মই হোক আপনার শরণ। “কুকথা লোক বারংবার বলে, কিন্তু সৎপথ দেখানোর মানুষ এ জগতে কমই আছে। “চতুষ্কোণ পর্বতের অভ্যন্তরে আটকা পড়া মানুষ যেমন না পারে বেরোতে, না পারে থাকতে, তেমনি জরা, জন্ম, ব্যাধি, মৃত্যুর দুঃখময় পর্বতগাত্র থেকে আপন অন্তরে সদ্ধর্ম ব্যতীত মুক্তির অন্য পন্থা নেই।
“সকল প্রাচীন দিগ্বিজয়ী রাজচক্রবর্তীগণ, যাঁরা জগতে ঈশ্বরের ন্যায় বিরজ করতেন, তাঁরা মনে করতেন আপন শক্তিবলে ক্ষয় রোধ করবেন, ক্ষণকালের জীবনযাপনের পর তাঁরাও গত হয়েছেন। “আপনার রাজকীয় শকটের দিকে তাকিয়ে দেখুন, দেখবেন এতেও ব্যবহারাদি জনিত ক্ষয় ধরেছে; “কালাগ্নি সুমেরু পর্বতকে দ্রবীভূত করবে একদিন, এমনকি মহাসমুদ্রও শুষ্ক হবে, সে তুলনায় এই নশ্বর শরীর কতই না তুচ্ছ। বুদ্বুদতুল্য অনিত্য এ শরীর, সম্পদের আদর গায়ে মেখে জীবনের দীর্ঘ রাত্রির যাতনা সয়ে চলেছে, উদাসীন অলস জীবন, এ শরীর কতদিনই বা পৃথিবীতে থাকবে । হঠাৎ করে মৃত্যু আসে, নষ্ট হওয়া কাঠের নদীতে ভেসে যাওয়ার মতন করে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। “জলাভূমি হতে ঘন বাষ্প উথ্থিত হয়, ঝোড়ো হাওয়া তাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়, সূর্যের আলোকছটা সুমেরু পর্বতের চারপাশ ঘিরে থাকে, দাবাগ্নির লোলজিহ্বা জলাভূমি শুষে নেয়, তাবৎ সঞ্জাত বস্তুনিচয় বারংবার বিনাশের নিমিত্ত জন্মগ্রহণ করে।
“যিনি শিহিভূত, ধর্মপথে যিনি পিছপা নন, পরিবর্তনশীলতার এই প্রত্যাশায় তিনি তাবৎ প্রবৃত্তি থেকে নিজেকে মুক্ত করেন, তিনি আত্ম-প্রমোদে রত নন, জীবনে জটিলতায় তাঁর জীবন বাঁধা নেই, কোন বন্ধন নেই জীবনে, বন্ধুত্ব চান না, পাণ্ডিত্যের ধার ধারেন না, অথচ জগৎ থেকে নিজেকে পুরোপুরি সরিয়েও রাখেন না; কেননা তাঁর প্রজ্ঞা না-উপলব্ধির প্রজ্ঞা; অথচ জীবনের ক্ষণস্থায়িত্বকে উপলব্ধি করেন। “জ্ঞানীজন জানেন যে স্বর্গে জন্মেও আত্মা ও সময়ের চঞ্চলতা হতে, অস্তিত্বের বিনাশ হতে কারো নিস্তার নেই। তাঁরা তাই অপরিবর্তনীয় মানসের পাঠ নেন, কেননা, যা অপরিবর্তনীয়, তাতেই পরম শান্তি। “অমৃতময় জীবনের অপরিবর্তনীয় কায়া সকলেই প্রাপ্ত হয়, একেই মনোমায়াকায়া বলা হয়; সর্ব জীব সমাগত বুদ্ধ, কারণ সকল জীবই ন-শ্বর; আবার সকল জীবই বিগত বুদ্ধ কেননা সকল জীবই বিগতকালে ন-শ্বর; অতএব সত্যি বলতে কি, সমস্ত জীবই বুদ্ধ কারণ, সমস্ত জীবই ন-শ্বর। “এই নিয়ত পরিবর্তনশীল দেহধারণই সকল দুঃখের মূল। “হৃদয়ের কথা চিন্তা করুন মহারাজ, লোভ-লালসাকে দূর করুন; তখন আর দুঃখ থাকবে না। কামনা বাসনা সতত পরিবর্তনশীল, লালসাই কামনা, এরা যেন দ্রুতপদে চলমান দুই বৃষ, আবার যেখানে লালসা, সেখানে প্রেম নেই। “যে গাছে দাবানল জ্বলছে, সেখানে কি পাখিরা ফিরে আসে কোনদিন?
“জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ, দিব্যজ্ঞানী সাধু এই কথা না জানলে সাধু হবার যোগ্য নন।
“এই জ্ঞান উপেক্ষা করা জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল।
“একে কেন্দ্র করেই হোক সকল সম্প্রদায়ের শিক্ষা; একে বাদ দিয়ে সত্যিকারের কারণ বলে আর কিছু থাকে না।
এই কথা শুনে মহারাজ প্রসেনজিৎ প্রাসাদে ফিরে গেলেন, ও মহারাণীর সঙ্গে বিবাদ মিটিয়ে নিলেন। মহারাজের মন শান্ত হল, তিনি প্রসন্ন বোধ করলেন। তিনি শিখলেন যে যেখানে বিশ্বাস নেই সেখানেই অজ্ঞানতার পারাবার। আবার উল্টোপাল্টা বিশ্বাস হল লালসার ধেয়ে আসা বাণের জল; কিন্তু বোধি একটি তরী, সচেতন প্রতিফলন অনুধ্যান সেখানে যেন শক্ত করে বাঁধা কাছি যাকে ধরে তরী বেয়ে তরণীর ওপারে নির্মল প্রশান্তিতে যাওয়া যায়। কিন্তু এত সত্ত্বেও মহারাজ প্রসেনজিৎ না দিব্যজ্ঞানের অধিকারী, না তিনি বুদ্ধদেবকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতেন। শুধু তাই নয়, ধর্মবিশ্বাসের উৎসাহে, ধর্মোপদেশে যা পুণ্যার্জন করেছেন তার চেয়েও অতিরিক্ত পুণ্য প্রাপ্তি আশায় তিনি এক রাজসূয়যজ্ঞের হুকুম দিয়ে বসলেন।
সপ্তম অধ্যায়
পরম শ্রদ্ধেয় জন তখন অনাথপিণ্ডকের জেতবনে অবস্থান করছেন । একদল সন্ন্যাসী ভোরে উঠে সাজসজ্জা করে ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে আশ্রম থেকে শ্রাবস্তীনগরে মাধুকরীতে বেরিয়েছেন। ফিরে এসে তাঁরা বুদ্ধদেবের দর্শণ প্রার্থনা করলেন ও মহারাজ প্রসেনজিত যে মহাযজ্ঞের আয়োজন করেছেন সে সম্বন্ধে তাঁকে জানালেন। সেই যজ্ঞে পাঁচশো করে ষাঁড়, বকনা-বাছুর, ছাগ, মেষ, প্রভৃতি পশুকে বেঁধে যজ্ঞশালায় বলিদানের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তাদের পিছনে ক্রীতদাস ও সামান্য কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে এমন সব মানুষকে রীতিমত চাবকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, সে বেচারারা চোখের জল ফেলতে ফেলতে বলিদানের প্রস্তুতির কাজ করে যাচ্ছে, এই সব দৃশ্য তাঁরা স্বচক্ষে দেখে এসেছেন। এই রকম একটি অশুভ মারণযজ্ঞের আয়োজন হচ্ছে, এই কথা শুনে মহামানবের উপলব্ধি হল যে মানুষ চিরকাল কেবল মূর্খতা, অজ্ঞানতা, আর অচেতনতার কারণে অধঃপাতে যায়।
“মেষাদি পশু, যারা তাদের দুধ দিয়ে তোমাদের পাত্র ভরিয়ে রাখে, তাদের হত্যা করে, তাদের নিপীড়িত শরীরের মাংস ভক্ষণ অনিষ্টকর পাপকাজ। যে মূর্খ হাত সার্বিক শূন্যতায় কসাইয়ের ছুরি ধরে আছে, জন্ম জন্মান্তর ধরে সে শোণিতসিক্ত হয়ে ভুগবে । হে মোর ভ্রাতাগণ, ভিক্ষুগণ, আর কত পাপ, আর কত অনিষ্ট, আর কত সদয় ঋষভ ও অন্যান্য পশুদের হত্যালীলা, করুণ অসহায় তাদের যে দু-চোখ, আর কত উন্মত্ত হত্যালীলায় বলি দিয়ে রক্তপান চলবে, শুধু পুনর্জন্মের আশায়,বার বার সেই আত্ম স্বর্গ আর যন্ত্রণাভোগে ফিরে আসা!
“মানুষ যা কিছু যজ্ঞে উৎসর্গ করে, একবারে, কি দায়ে পড়ে সারা বছর ধরে, পুণ্যলাভের আশায়, সেসবের মূল্য এক কানাকড়িও নয়।
“সমস্ত প্রাণী শাস্তির ভয়ে কম্পিত, সমস্ত প্রাণীই বাঁচতে ভালবাসে, মনে রেখো তোমরাও সেই অন্যান্য প্রাণী অপেক্ষা পৃথক কিছু নও, অতএব হত্যা কর না, আর কাউকে বলি হতে দিও না।
“যে মানুষ আপন সুখের নিমিত্ত অন্যান্য প্রাণী যারা সুখের সন্ধান করে, তাদের হত্যা করে নিজে সুখ পেতে চায়, সেও কখনোই মৃত্যুর পরে সুখ লাভ করবে না।
“যিনি অন্য জীবিত প্রাণীকে আঘাত করেন তিনি ধার্মিক নন; যে মানুষ অন্য প্রাণীর প্রতি করুণা করেন, তিনিই প্রকৃত ধার্মিক।
“আমরা তো যন্ত্রণা থেকেই উত্তরণ চাই, তবে কেন আমরা অন্যদের যন্ত্রণা দেব?
“মনকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে যাতে নিষ্ঠুরতা, নির্দয় হত্যার চিন্তামাত্র ঘৃণার উদ্রেক করবে। তা না হলে জন্ম জন্মান্তরের দুঃখভোগের বন্ধন থেকে মুক্তি নেই।
“নিতান্ত আন্তরিক সাধু-সন্ন্যাসী, জ্ঞানীজন, তাঁরা যখন খুব সরু একটা পথ ধরে হাঁটবেন, তখনো, পথের দুপাশে গজিয়ে ওঠা তৃণেও যেন না পা পড়ে, সেইভাবে সন্তর্পণে পদচারণা করবেন।
“এই ধরণের একান্ত আন্তরিক ভিক্ষুগণেরই মোক্ষ লাভ হবে, যাঁরা পূর্বজন্মকৃতকর্মের ঋণ শোধ করেছেন, যাঁরা আর কোনভাবেই মনন, সহন, পীড়নের ত্রিজগতে আর আবদ্ধ নন ।
“ধার্মিক মানুষ, যিনি অন্যের মুক্তির আশা করেন, তিনি কি করে পশুমাংস ভক্ষণ করে নিজে বেঁচে থাকার কথা ভাবেন, বা ভাবেন কি করে যে পরজন্মে কিছু লাভ করবেন?
“তাই ধর্মে নিবেদিতপ্রাণ মানুষ এই একটা ব্যাপারে যত্নবান হবেন যে, কারুর প্রতি সামান্যতম নিষ্ঠুরতাটুকু প্রদর্শণ করবেন না।”
রাজার কানে এই সমস্ত কথা গেল। মহারাজ শুনলেন যে বুদ্ধদেব যাগযজ্ঞ-বলিদানকে কসাইগিরি অপেক্ষা কিছু মনে করেন না। মহারাজ আবার বুদ্ধদেবের সকাশে এলেন। বুদ্ধদেবকে প্রণাম করলেন, কুশল জিজ্ঞাসা করলেন, করে তাঁর পাশে বসলেন।
“মহাত্মা গৌতম কি মনে করেন না যে তিনি সার্বিক ও দিব্যজ্ঞান লাভ করেছেন?”
“যথার্থ দিব্যজ্ঞানী যদি কেউ থাকেন, তো সে আমিই। আমি নির্দ্বিধায় ঘোষণা করছি যে আমি সম্যকরূপে বোধিপ্রাপ্ত, দিব্যজ্ঞানী।”
“কিন্তু প্রভু গৌতম, আপনার মতন আরো কত সাধু সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁদের নিজস্ব সম্প্রদায়ও আছে, শিষ্য শিষ্যারা আছেন, মহা তত্ববিদ সব পণ্ডিত রয়েছেন। আমি যখন তাঁদেরও এই একই প্রশ্ন করি, কই তাঁরা তো দাবী করেন না যে তাঁরা সম্যকরূপে বোধিপ্রাপ্ত। তাহলে? মহামতি গৌতম বয়েসে নবীন, ধর্মপথেও নবীনই বলা চলে।”
“নবীন, এই কারণে, চারটি প্রাণীকে কখনো অবজ্ঞা বা তাচ্ছিল্য করতে নেই,” বুদ্ধদেব বললেন, “জানেন কি তাঁরা কারা?
“রাজপুত্র।
“সর্প ।
“অগ্নি ।
“সন্ন্যাসী ।
“মহারাজ, নবীন বলে এই চার প্রাণীকে কখনো তাচ্ছিল্য বা অবজ্ঞা করতে নেই।”
এই কথা শুনে মহারাজ প্রসেনজিৎ বললেন,
“ধন্য, প্রভু, ধন্য! যেন লুপ্ত বস্তু উদ্ধার করা হল, যেন পথহারা পথিককে পথ প্রদর্শন করা হল, যেন তমিস্রায় আলোকবর্তিকা প্রজ্জ্বলিত হল যাতে চক্ষুষ্মান মানুষ বহিরঙ্গের রূপ দর্শণ করতে পারে, তেমন, আপনি, হে প্রভু, আমার সামনে সত্যের উন্মোচন করলেন। আমিও ধর্মে ও সংঘে শরণ নিলাম। পরমজন যেন আমায় শিষ্যত্বে গ্রহণ করেন; আজ হতে আজীবন আমি আপনার শরণ নিলাম।” মহারাজ প্রসেনজিৎ কথা রেখেছিলেন। বুদ্ধদেব ও মহারাজ প্রসেনজিৎ সমসাময়িক জীবন অতিবাহিত করেছিলেন।
আলোকিত জন খুব সহজ সরল জীবনযাপন করতেন। উষাকালে উঠতেন, ওঠার পর কারো সাহায্য ছাড়াই স্নান-সজ্জা সারতেন । তারপর প্রাত্যহিক খাবার সময় পর্যন্ত একাকী ধ্যান করতেন। যখন খাবার সময় হত, যথাযথ পোষাক পরিধান করে, ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে, একাকী বা শিষ্য পরিবৃত হয়ে নগরে কি গ্রামে বেরিয়ে পড়তেন। বেরিয়ে যে গৃহে অন্ন গ্রহণ করতেন, সেখানকার গৃহস্বামী ও গৃহের অন্যান্যদের সঙ্গে তারা যতটুকু বুঝতে পারত, সেই অনুযায়ী, আধ্যাত্মিক আলোচনা করতেন। আশ্রমে ফিরে এসে হয় তাঁর আসনে বসে থাকতেন, নাহলে বৃষ্টির সময় কুটিরে অপেক্ষা করতেন যতক্ষণ না পর্যন্ত সমস্ত আশ্রমিক, সাধুরা তাঁদের খাওয়া শেষ করতেন । তারপর আশ্রমিকদের তত্বশিক্ষা দিতেন। না হলে কি বিষয়ে ধ্যান করতে হবে বলে দিতেন। বা তাদের সব রকম চিন্তাকে স্তব্ধ করার শিক্ষা দিতেন, মনকে সব রকম চিন্তা থেকে নিরত করার উপদেশ দিতেন, এমনকি সমস্ত চিন্তার উৎস যে চিন্তা, তাকেও স্তব্ধ করার উপদেশ দিতেন, এই চর্চাই নির্বাণের পথের পাথেয়। শিষ্যরা তারপর তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিতেন, নিয়ে যে যার আপন পছন্দমত জায়গায় গিয়ে ধ্যান করতেন। যখন খুব গরম পড়ত, তখন বুদ্ধদেব শুয়ে সামান্য বিশ্রাম নিতেন, ডান পাশে কাত হয়ে শুয়ে (সিংহাসন অবস্থায়), এক জানুর ওপর আরেক জানু রেখে, মাথার তলায় হাত রেখে শুতেন। সবাইকে বুদ্ধদেব এইভাবেই শুয়ে থাকতে পরামর্শ দিতেন, নিজেও এইভাবে শুয়ে থাকতেন বলে তাঁকে কখনো কখনো শাক্যসিংহ নামেও অভিহিত করা হত। দুপুরে এই যে অবস্থায় শুয়ে থাকতেন, তিনি কিন্তু ঘুমোতেন না, এমনকি ধ্যানও করতেন না, বিশ্রামের সময় শুধুই বিশ্রাম করতেন। বিশ্রামই তখন একমাত্র বিষয়।
দ্বিপ্রহরে আশেপাশের গ্রাম নগর থেকে যারা দেখা করতে আসত তাদের সঙ্গে বক্তৃতার ঘরে দেখা করতেন; না হলে গাছের ছায়ায় তাদের সঙ্গে দেখা করতেন। তাদের প্রতি বুদ্ধদেবের অপার করুণা, যার যেমন বুদ্ধি-সামর্থ্য, প্রয়োজন, সেই অনুযায়ী তাদের উপদেশ দিতেন। যেমন একবার, এই রকম একটা সাক্ষাতে, বিশাখা নামে এক নারী একপাশে বসে উচ্চস্বরে রোদন করছিলেন। তাঁর নাতনি সদ্য মারা গেছে, এই শোক তিনি সহ্য করতে পারছিলেন না, তাই বুদ্ধদেবের কাছে এসে অঝোরে অশ্রুপাত করছেন। বুদ্ধদেব তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন শ্রাবস্তীনগরে কতজন থাকেন।
“ভগবান, লোকে বলে সাত গুণ এক কোটি লোক থাকে”
“ধর সবাই যদি তোমার নাতনির মত হত, তাদের ভালবাসতে না?”
“নিশ্চয়ই বাসতাম প্রভু।”
“আর শ্রাবস্তীনগরে দিনে কত লোক মারা যায় জান?”
“বহু লোক, প্রভু।”
“তাহলে তো কখনো এমন সময় হবে না যখন তুমি কারো না কারোর জন্য কান্নাকাটি করবে না।”
“ঠিক বলেছেন, প্রভু।”
“তবে কি দিবারাত্র কান্নাকাটি করেই জীবন কাটাবে?”
“বুঝেছি প্রভু, ঠিক বলেছেন।”
“এখন আর শোক কোর না।”
দিনের শেষে, যেদিন প্রয়োজন হত, স্নান করতেন। করে, কয়েকজন শিষ্যকে নিয়ে ধর্মতত্বের কূট বিষয়সমূহ আলোচনা করতেন। মনস্তত্বের কি কৌশলে নানান মানুষের নানান বদ্ধ ধারণা, প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে ধর্মতত্বের নানান দিক কি করে বোঝান যায় তাই দেখাতেন, শেখাতেন। “বুদ্ধগণ নানা উপায়ে নানান যন্ত্রে তাঁদের প্রকৌশল প্রকাশ করেন, তথাপি বুদ্ধরূপী যান একমেবাদ্বিতীয়ম, সেখানে তূরীয় শান্তি।
মরদেহের ইহজন্মের কি বিগত জন্মের সকল প্রকার আচার আচরণই বুদ্ধগণ অবগত আছেন, তাই বিভিন্ন পন্থায় তাঁরা মানুষকে আলো দেখান। এমনই তাঁদের ধীশক্তি।”
বুদ্ধদেব রাত্রির প্রথম প্রহর এইভাবে শিক্ষা দিয়ে অতিবাহিত করতেন। কখনো কখনো সাধুদের কাছে চলে যেতেন, গিয়ে জিজ্ঞাসা করতেন, “কি নিয়ে আলোচনা করছেন সাধুগণ, কি নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?”
বাকী সন্ধ্যে বারান্দায় বা সামনে পায়চারি করতেন, ধ্যান করতেন, আনন্দ তাঁর পিছনে তাঁকে পায়চারি করে অনুসরণ করতেন।
বুদ্ধদেব বলতেন, “যদি কোন মানুষ নিজেকে গুরুত্ব দিয়ে বিচার করতে চান, তাঁকে নিজের দিকে সাবধানে নজর দিতে হবে। রাত্রির তিন প্রহরের অন্তত এক প্রহরে জ্ঞানীজন নিজের প্রতি নজর রাখেন।”
তারপর রাতে শুয়ে পড়তেন।
“একান্ত বসনে, একাকী শয়নে, একাকী পদচারণায়, এবং একাকী নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে, অরণ্যের প্রান্তদেশে, মানুষ সুখী হোক”, একথা ধম্মপদ (ধর্মের পদচারণা) বলেছেন।
“কূপ খননকারীরা যেমন যেখানে চায়, সেখানে তারা জলকে নিয়ে যেতে পারে; ব্যাধ যেমন ইচ্ছে তেমন করে শর প্রক্ষেপ করে, সূত্রধর নিজের ইচ্ছামত কাঠ কেটে আসবাব তৈরী করতে পারে, মহৎ লোকও তেমনি নিজেই নিজেকে গড়ে নিতে পারেন।” — ধম্মপদ
অষ্টম অধ্যায়
একদিন আনন্দ পরমারাধ্য জনকে জিজ্ঞাসা করলেন নারীদের উপস্থিতিতে তাঁদের সঙ্গে কেমন ভাবে আচরণ করতে হয়।
“তাঁদের সম্পূর্ণরূপে পরিহার কর, আনন্দ।”
“কিন্তু প্রভু, তাঁরা যদি আমাদের কাছে আসেন?”
“তাঁদের সঙ্গে বাক্যালাপ কর না আনন্দ।”
“তাঁরা যদি প্রশ্ন করেন, তখন?”
“সদাজাগ্রত থাকবে, আনন্দ।”
তারপর পরম জন বললেন, “যখন নারীদের সঙ্গে বাক্যালাপ করবে, তাঁরা যদি বয়োজ্যেষ্ঠা হন, তাঁদের মাতৃজ্ঞানে সম্বোধন করবে, তাঁরা যদি বয়ঃকনিষ্ঠা হন, তাঁদের ভগ্নিসমা জ্ঞান করবে।”
আম্র নামে এক সুন্দরী নগরবধু, বৈশালীর ধনাঢ্য বণিকদের কাছ থেকে প্রচুর অর্থলাভ করেছিলেন। তাঁর মনোবাসনা তাঁর বিশাল প্রাসাদ ও আম্রকুঞ্জ বুদ্ধদেব ও তাঁর শিষ্যদের দান করেন। আম্র পরমাসুন্দরী, প্রস্ফুটিত গোলাপ ফুলের ন্যায় তাঁর গাত্রবর্ণ, তায় সঙ্গীত-নৃত্য পটিয়সী; উচ্চশ্রেণীর নারীর রূপকলা যা থাকে তাঁর সবই ছিল, তবুও আম্র নিজের জীবন সদ্ধর্মে উৎসর্গ করতে চাইছিলেন। তিনি মহৎ জনের কাছে তাঁর শিষ্যদের জন্য প্রাসাদ ও কানন দান করবেন এই বার্তা পেশ করলেন। বুদ্ধদেব তা সমাদরে গ্রহণ করলেন। আম্রকাননে একদিন বুদ্ধদেব উপবেশন করছেন, এমন সময় আম্র বার্তা পাঠালেন যে তিনি দেখা করতে চান। বুদ্ধদেব রাজি হলেন। আম্র তখন সপারিষদ দর্শণের পথে আসছেন।
“এই যে রমণী,” সমবেত শিষ্যদের বুদ্ধদেব বললেন, “ইনি অসামান্যা সুন্দরী, ধর্মপথের পথিক মানুষদের মুগ্ধ করার ক্ষমতা ধরেন; অতএব আপন আপন মস্তিষ্ক স্থির রাখবেন! আপন প্রজ্ঞায় অবিচল ও নিবেশিত থাকবেন আপনারা।”
“নারীসঙ্গে লিপ্সায় আপ্লুত, উত্তেজিত, কামোন্মত্ত হয়ে তাঁদের অভিপ্রায় আর মোহজালে আবদ্ধ হওয়ার চেয়ে বরং বাঘের মুখে কি ঘাতকের তরবারীর কোপে পড়াও শ্রেয়। তাঁদের অভিপ্রায় জন্মের অভিপ্রায়, মৃত্যুর ফাঁদ পাতা তাতে।
“সচল কি স্থির হয়ে, বসে কি শুয়ে, নারী তাঁর রূপ প্রদর্শণ করতে চান।
“পুরুষ স্বভাবত কাম মোহ থেকে মুক্ত নয়; পূর্ব কর্মফলহেতু সে কামজনিত কার্য থেকে মুক্ত নয়। আবার নারী জন্মদাত্রী, পুনর্জন্মের আধার; পরস্পর পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে, কর্মহেতু পরস্পর পরস্পরের শিকার; পরস্পর পরস্পরের নিমিত্ত কর্মেই যেন মিলিত ও বিচ্ছিন্ন; তাতে কোন “আমিত্ব” নেই না বলার, অহং, আনন্দ, আর মৃত্যরূপ যাঁতাকলের চাকায় ক্রমাগত নিষ্পেষিত হতে হতে তারা ঘুর্ণায়মান ।
“তবে এ কেমন ধরনের আনন্দ, শূন্যতাকে আলিঙ্গন করে ইন্দ্রিয়কে তৃপ্ত করার অসম্ভব প্রয়াস। উন্মত্ত হৃদয়ের কোন তৃপ্তি নেই, কোন কিছুতেই সে তুষ্ট হয় না। কোমরভাঙ্গা প্রয়াসেও সে তৃপ্ত হয়না।
“জীবনের পাত্র তলশূন্য এক বিভীষিকা, এ যেন স্বপ্নময় অবাস্তবতা, কারণাতীত তৃষ্ণার নিবারণহেতু বৃথা সুরাপান। অবাস্তব, অসম্ভব।
“মহাশূন্য আকাশের পানে তাকান! কামোন্মত্ত মানুষ কেমন করে একমুঠো আকাশ করতলগত করবে?
“ঐ স্বপ্ন দেখতে থাকা জড়বৎ মানুষটা কি উপায়ে অবধ্যকে বধ করবে?
“সর্বদিকে সকলই সদাসর্বদা শূন্যময়, জাগো, জেগে ওঠ!
“মন নির্বোধ, মনের ক্ষমতা সীমিত, এই সমস্তই যেন স্বপ্নে দেখা অলীক বিষয়কে বাস্তব বলে ভ্রম করা। যেন, সমুদ্রের গভীরতা অজ্ঞানতারূপী বায়ুপ্রবাহে আন্দোলিত হয়ে চলেছে ।
“নারী জন্ম দিতে চায়, কর্মহেতু সে একাকীত্ব ও বন্ধ্যাত্বকে ভয় পায়, অথচ এ পৃথিবী বন্ধ্যা নারীর সন্তান অপেক্ষা কিছুমাত্র অধিক বাস্তব নয়।
“চিত্রার্পিত হলেও নারী তার রূপের, সৌন্দর্য্যের প্রদর্শনকেই সবচেয়ে অধিক গুরুত্ব দেন, অতএব পুরুষের হৃদয়হরণ।
“কি উপায়ে নিজেদের সংযত রাখবেন? নারীর অশ্রুজল ও ওষ্ঠাধরের হাসি উভয়কেই শত্রুবৎ জ্ঞান করবেন, মনে রাখবেন নারীর ন্যুব্জ অবয়ব, আনত বাহুডোর, বিক্ষিপ্ত কেশদাম, এ সমস্তই পুরুষের হৃদয়হরণের উপায়।
“তাই যদি হয়, না জানি তাঁর সযত্ন লালিত সৌন্দর্যের প্রতি আরো কত না সতর্ক হওয়া চাই; বিশেষ করে তিনি যখন তাঁর রমণীয় আভরণসম্বলিত শরীর প্রদর্শণ করে মূর্খ পুরুষের সঙ্গে হাস্যরস করবেন, তখন তো বিশেষ করেই সতর্ক হওয়া চাই।
“আহ, অনিত্য শরীরের দূঃখরূপ, ভয়ংকর কদর্য অবয়ব অনুধাবন না করতে পেরে শুধু বহিরঙ্গের কথা ভেবে ভেবে মন কতই না কুচিন্তায়, কত না চাঞ্চল্যে আন্দোলিত হয়।
“অথচ শরীরের অভ্যন্তরের এই কদর্য রূপ বিবেচনা করলে সমস্ত কামলালসাগত মনোবৃত্তির অন্ত হয়।
“এই বিষয়সমূহ যথাযথ বিবেচনা করলে, এদের সীমা পরিসীমার কথা খেয়াল রাখলে দেখবেন স্বর্গের অপ্সরাদের দেখলেও আর কামজনিত আমোদের উদয় হবে না।
“যদিও পুরুষের কামভাব প্রবল, এই কামের প্রাবল্যকেই ভয় পেতে হয়। অতএব আন্তরিক চেষ্টারূপী ধনুর্বাণ হাতে তুলে নিন, তার জ্যা-তে পূর্ণজ্ঞানের শলাকারূপী শর রোপন করুন, সৎ চিন্তার শিরস্ত্রাণে মস্তকে আবৃত করে পঞ্চকামের বিরুদ্ধে স্থিরসঙ্কল্প হয়ে যুদ্ধে রত হন।
“নারী দেহ দর্শণমাত্রে মনে কামভাবের উদয়, কি নারীর প্রতি কামলোলুপ দৃষ্টি প্রক্ষেপণ, এ অপেক্ষা লৌহতপ্ত শলাকায় চোখ উপড়ানো শ্রেয়স্কর!
“নারীর দেহ সৌন্দর্য্যের প্রতি কামভাবে পুরুষের মন কলুষিত হয়। পৌরুষ এমনই যে কর্মহেতু পুরুষের মন স্বভাবত দগ্ধ হয়; তখন জীবনের শেষপ্রান্তে উপনীত হয়ে, সারাজীবন নারীসঙ্গে নিজেকে নিম্নগামী করে, কামলালসার ফাঁদে পড়ে পুরুষ কুপথে যায়।
“সারাজীবন ক্ষুদ্র গৃহকোণে অতিবাহিত করে বার্ধক্যে সে যখন উপনীত হয়, তখন তার মুখে হাজারো ধর্মের মন্ত্র, তখন কতই না তার অনুতাপ।
“ভয় পেতে হলে কুমতিপূর্ণ সেই অনুতাপের দিনগুলোকে ভয় পান। ত্রস্ত হন, নিজের মনে নারীর ছলনাকে প্রশ্রয় দেবেন না।
“সাধুর যেন পুনর্জন্ম না হয়; দ্বাদশ কথার অর্থ যেমন বারো, তেমন জন্ম মানেই মৃত্যু!
“মন স্থির রাখুন, নারীর দেহের দিকে কামদৃষ্টি কখনো নিক্ষেপ করবেন না।
“একবার মনে মনে কল্পনা করুন ব্রাহ্মণ কি কায়স্থ কি ক্ষত্রিয় গোত্রের একটি পনেরো কি ষোল বছরের কিশোরীর ন্যায় ভরা যৌবনবতী এক রমণী; না তিনি দীর্ঘাঙ্গী, না তিনি খর্বকায়া; না তিনি কৃশা, না তিনি স্থুলকায়া; না তিনি কৃষ্ণা, না তিনি অতি উজ্জ্বলবর্ণা; এই রূপে তিনি কি অপরূপা নন? এই রূপ দর্শণে মনে যে আনন্দের বোধ উদয় হয় — সে আনন্দ শুধুই বহিরঙ্গজনিত আনন্দ।
“এখন কল্পনা করুন, সেই একই রমণী, এবার তিনি অশীতিপর, কি নবতিপর, কি শতবর্ষ তাঁর বয়স; এখন তিনি লোলচর্মা, বয়সের ভারে ন্যুব্জা, শীর্ণা, ভগ্নদন্তা, কোনমতে যষ্টিতে ভর করে চলেছেন; কি মনে হয় তখন, সাধুগণ? তাঁর পূর্বের সেই রূপমাধুরী এখন সকলই অস্তমিত — এখন তাঁর হীনাবস্থা, তাই নয়?
“আবার, এই রমণী, কল্পনা করুন, অসুস্থ, সর্বাঙ্গে ক্ষতবিক্ষত শরীর, অন্যের উপর নির্ভরশীল, কোনমতে বেঁচে আছেন — কি মনে হয় সাধুগণ? তাঁর পূর্বের সেই রূপমাধুরী এখন সকলই বিগত — এখন তাঁর হীনাবস্থা, তাই নয়?
“আবার কল্পনা করুন, এই রমণীর দেহ, শ্মশানে পড়ে আছে, একদিন, দুদিন, তিনদিন হয়ে গেছে, বর্ণহীন, শরীর ফুলে গেছে, পচন ধরেছে, কাক-পক্ষীতে, শেয়ালে কুকুরে টানাটানি করে ঠুকরে খাচ্ছে, নয়ত রক্তাক্ত কঙ্কাল, সেখান থেকে মাংসের টুকরো ঝুলছে, নয়ত, অস্থিসমূহ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত, কোথাও বা স্তুপীকৃত হয়ে পড়ে আছে, এই করে বছরভর পার হয়ে গেল, হাড় মাংস ধুলোয় মিশে যাচ্ছে দিন কে দিন।
“তখন কি মনে হয়, সাধুগণ?
“এই যে সেই সময়ের, যুবা বয়সের দিব্যকান্তি — কোথায় সে সব হারিয়ে গেছে, এখন তার জায়গায় হীন অবয়ব।
‘তথাপি, এই সার সত্য। দেহের, অবয়বের এই হীনতা। হন্যমান শরীর।”
আম্র আশ্রমে আসছেন, সেই মত সজ্জিতা হয়ে এলেন। অতি সাধারণ বস্ত্র পরিধান করে, যাতে কারো মনে উত্তেজনার লেশমাত্র না উদয় হয়, নিরাভরণ সাজসজ্জা করে বুদ্ধদেবের কাছে শান্ত মনে এলেন। সঙ্গে করে মহৎ জন ও তাঁর শিষ্যদের জন্য খাদ্য ও পানীয় নিয়ে এলেন। বুদ্ধদেব তাঁকে সমাদর করে বললেন, “হে নারী! আপনার হৃদয় শান্ত ও স্বচ্ছ, আপনার অবয়ব নিরাভরণ; আপনি বয়সে কনিষ্ঠা ও ধনসম্পদে পরিপূর্ণা, আপনি সুন্দরী ও প্রতিভাময়ী;
“এমন একজন মানুষ, যিনি যথার্থই ধর্ম গ্রহণ করতে প্রস্তুত, সত্যি বলতে কি, সহজে এমন মানুষের দেখা মেলে না।
“যিনি মহাপণ্ডিত, তিনি পূর্বজন্মহেতু প্রজ্ঞাবান হয়ে জন্মেছেন, তিনি পরমানন্দে ধর্মপথ অবলম্বন করছেন, এ দেখতে পাওয়া যায়; কিন্তু নারী, যাঁরা সংকল্পে দৃঢ় নন, সাধারণ যাঁদের প্রজ্ঞা, যাঁরা প্রেমে তদ্গত, আবার এদিকে পুণ্যচিত্তের অধিকারী, এমন মানুষের সহজে দেখা মেলে না।
“জগতে পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। যথাযথ চিন্তায় একান্তে ধর্মে আনন্দ প্রকাশ করেন, অর্থ ও রূপের অনিত্যতা সম্বন্ধে অবধান করেন, তারপর ধর্মকেই শ্রেষ্ঠ আভরণ বলে স্বীকার করেন। “এমন পুরুষ মনে করেন, জগতের দোষ এই পথেই স্খালন করা সম্ভব; মনে করেন বাল-বৃদ্ধের জীবনের অবস্থার পরিবর্তন এই পথেই হবে। ধর্মপথে চললে, অন্য লোকের যে দুরবস্থা, তাতে তিনি পড়বেন না, তা তাঁকে স্পর্শ করবে না, এই তাঁর বিশ্বাস।
“তবে তাঁকেও দুঃখ ভোগ করতে হয়, যেহেতু বহির্জগতের ওপর নির্ভর করেন। যেখানে তিনি আপন শক্তিতে ভাস্বর, সেখানে তিনি পরমানন্দ অনুভব করেন।
“কিন্তু নারীর ক্ষেত্রে অন্যরকম। তাঁর প্রসববেদনার কারণ অপর কেউ; অপরের ঔরসজাত সন্তানের তিনি ধাত্রী; এইসব বিবেচনা করলে নারীকে দূরে সরিয়ে রাখাই বিধেয়।”
অম্রা বললেন, “হে করুণাময় প্রভু! আমি অজ্ঞান নারী; তবুও একান্ত আন্তরিক ভাবে নিজেকে দান করতে চাই।” এই কথা বলে তিনি ভিক্ষুণিসংঘে যোগদান করলেন।
নবম অধ্যায়
বৈশালী থেকে পরম পুণ্যজন এবার শ্রাবস্তী নগরে গেলেন। এইখানে জেতবনের ধ্যানগৃহে বুদ্ধদেব তাঁর বারোশো শিষ্যকে সুরঙ্গমা সূত্র শিক্ষা দিয়েছিলেন । সুরঙ্গমা সূত্র এক মহৎ শিক্ষা যা শ্রবণ করে শিষ্যদের মনের নানা রকমের বিহ্বলতা, নানা প্রশ্নের সমাধান মিলেছিল। যাঁরা মার্গে অপেক্ষাকৃত অগ্রসর সন্ন্যাসী, তাঁরা তাঁদের ধ্যানের সময় নানা রকমের সন্দেহের, নানা রকমের তাত্ত্বিক সমস্যার সম্মুখীন হতেন; সুরঙ্গমা সূত্রের অবতারণায় তাঁদের সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর মিলেছিল ও সন্দেহের নিরসন হয়েছিল। পরম জন বড় যত্ন সহকারে এই মহাসূত্রের অবতারণা ও ব্যাখ্যা করেছিলেন। এই সূত্র এক পরম সূত্র; এই সূত্রই তথাগতের নিগূঢ় পন্থা; সেই মহাসূত্র শ্রবণ করে নবীন সন্ন্যাসীগণও পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করলেন, ও তৎক্ষণাৎ অপার জ্ঞানের পারাবারে অবগাহন করলেন।
আনন্দকে কেন্দ্র করে সেদিন একটা অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটেছিল। এবং এই ঘটনাকে নিয়েই তত্ত্ব আলোচনার সূত্রপাত। মহারাজ প্রসেনজিৎ সেই দিন সকালে বুদ্ধদেব ও তাঁর প্রধান বোধিসত্ত্ব-মহাসত্ত্বদের (এঁরা পরম জ্ঞানীজন) তাঁর রাজপ্রাসাদে একটি বিশেষ ভোজসভায় আমন্ত্রণ করেছিলেন। আনন্দ সে সময়ে জেতবন থেকে দূরে অন্য কোন এক প্রদেশে কার্যোপলক্ষে গিয়েছিলেন। নবীন, প্রবীণ, সমস্ত সাধুদের অন্য একটি জায়গায় নিমন্ত্রণ ছিল।
আনন্দ ফিরে এসে দেখেন আশ্রমে কেউ নেই। তাই তিনি শ্রাবস্তীনগরে ভিক্ষাপাত্র হাতে অন্নের অন্বেষণে মাধুকরী করতে বেরিয়ে পড়লেন। গৈরিক বসন পরিহিত সুদর্শণ আনন্দ ভিক্ষাপাত্র হাতে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করছেন, এই দৃশ্য দেখে জনৈকা বারবণিতার প্রকৃতি নামে সুন্দরী যুবতী কন্যা তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হল। প্রকৃতি তার মায়ের কাছে আব্দার করে বসল যে তিনি যেন যে কোন উপায়ে, যে কোন মায়াবলে, এই অনিন্দ্যকান্তি যুবক সন্ন্যাসীটিকে তাদের গৃহে, তার কক্ষে নিয়ে আসেন। আনন্দ দিব্যকান্তি, পরম রমণীয়, তার স্বভাব উষ্ণ; ফলে যা হবার হল, প্রকৃতির মায়ের ভ্রমণিকা মায়ার খেলায় পড়ে আর প্রকৃতির সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে সে কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রকৃতির কক্ষে হাজির হল।
বুদ্ধদেব ততক্ষণে ধ্যানগৃহে ফিরে এসেছেন। এসে সাধুদের সঙ্গে বসে তাদের গ্রীষ্মকালীন ধ্যান প্রার্থনা নিয়ে আলোচনা করছেন, কোন কোন সাধু তাঁদের উপশথ স্বীকারোক্তি করবেন তার প্রস্তুতি হচ্ছে; এদিকে বুদ্ধদেব কিন্তু আনন্দ কোথায় কি করছেন, তাঁর সঙ্গে কি হচ্ছে, সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অবগত ছিলেন। সেইমত, তিনি তাঁর “অন্য আনন্দ”, তাঁর সবর্ক্ষণের সঙ্গী, জ্ঞানালোক বিচ্ছুরণকারী মহা বোধিসত্ত্ব, মঞ্জুশ্রীকে, ধরণী মন্ত্র উচ্চারণের নির্দেশ দিয়ে, প্রকৃতিদের বারগৃহে পাঠিয়ে দিলেন, যাতে আনন্দ যেন মোহজালে আচ্ছন্ন না হয়ে পড়েন, কোন প্রলোভনে পা না দিয়ে বসেন। যেই মঞ্জুশ্রী প্রভুর নির্দেশ অনুযায়ী ধরণীমন্ত্র উচ্চারণ করলেন, আনন্দ অমনি তাঁর সম্বিৎ ফিরে পেলেন, ও উপলব্ধি করলেন যে তিনি স্বপ্ন মায়ায় আচ্ছন্ন। মঞ্জুশ্রী তখন আনন্দ আর প্রকৃতি, দুজনকেই বুদ্ধের কাছে ফিরে যেতে পরামর্শ দিলেন ও তাঁরা দুজনে মঞ্জুশ্রীর সঙ্গে বুদ্ধদেবের কাছে ধ্যানগৃহে ফিরে গেলেন।
আনন্দ বুদ্ধদেবের কাছে ফিরে এসে পরম শ্রদ্ধাভরে আভূমি প্রণত হলেন। প্রণাম করে আনন্দ নিজেকে দোষ দিয়ে বললেন, তাঁর এখনো সম্যক আলোকপ্রাপ্তি হয়নি, ছি ছি, এ কি করলেন, তাঁর যে সৎ চিৎ, পরমাপ্রকৃতি, সেই স্বরূপ কে আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে মোহজাল তাকে উত্তোলন করে তাঁর স্বরূপ উন্মোচন করতে পারলেন না; পারলেন না কেননা তাঁর পূর্বজন্মের প্রথম থেকেই তিনি বড় বেশী শব্দ-বাক্যের পঠন পাঠনেই সময় দিয়েছেন; কাজেই সম্যক স্থিতিশীলতা আর অটল স্থিতাবস্থায়, যা অপার শান্তির পারাবার, তাতে তাঁর মন সংযুক্ত হতে পারেনি। তাই তিনিও প্রকৃতির মোহ কাটাতে পারেননি, নিজের মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে অক্ষম, নিজের শরীরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেন না, না করে জন্ম মৃত্যুর ক্রমাগত বয়ে চলা কালচক্রের পাশবিক প্রবৃত্তিতে তিনিও জড়িয়ে পড়লেন, বহির্জগতের আকর্ষণে, ভিক্ষুজীবন ছেড়ে।
আনন্দ বুদ্ধের কাছে আকুল ভাবে প্রার্থনা করতে লাগলেন, দশদিকে অপরাপর তথাগতগণের প্রতি প্রার্থনা করলেন, যেন তিনি সম্যক বোধি প্রাপ্ত হতে পারেন। এই সম্যক বোধি তিনটি পরম গুণের সমষ্টি — ধ্যান, সমাধি, ও সমাপত্তি (ধ্যানে যে তূরীয় অবস্থা প্রাপ্তি হয়, সমাপত্তি সেই অতীন্দ্রিয়বোধ)। সেই সভাগৃহে সমবেত জনতা একযোগে ও উৎসুকচিত্তে অপেক্ষা করে রইলেন বুদ্ধদেব আনন্দকে কি বলেন দেখবার জন্য। একযোগে সকলে গুরুদেব কে প্রণিপাত করে যে যার আসন গ্রহণ করলেন। সকলে নিঃশব্দে শান্ত মনে বুদ্ধদেবের পুণ্য শিক্ষার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন ।
বুদ্ধদেব বললেন, “আনন্দ! ও আর যারা যারা আজ এই মহৎ ধর্ম সমাবেশে উপস্থিত আছেন! আপনারা সকলে নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে কি কারণে জীবাত্মা অনাদি অনন্তকাল জন্ম জন্মান্তর ধরে জন্ম-মৃত্যু-পুনর্জন্মের কালচক্রে আবর্তিত হয়ে চলেছে । কারণ তারা পরম মানসের সার তত্ত্ব আর তার সপ্রভ উজ্জ্বল জ্যোতি কখনো উপলব্ধি করেনি। বরং চিরকাল ধরে তারা মিথ্যা অহংবোধ, মায়া আর ক্ষণিকের অতি সাধারণ চিন্তায় নিজেদের ব্যস্ত রেখেছে। এমন করে অনাদি অনন্তকাল ধরে মৃত্যু আর পুনর্জন্মের কালচক্রে ক্রমাগত নিজেদের জড়িয়ে রেখেছে।
“অথচ মানুষের উচিৎ তথাগতের সঙ্গে একাত্ম হবার; তথাগতগণ অনাদি-অনন্তকাল ধরে তথতায় নিবেশিত; তাঁরা সর্বপ্রকার মানসজ জটিলতায় অনুদ্বিগ্ন, স্থিতচেতন; ইতস্তত বিক্ষিপ্ত উথ্থিত চিন্তায় তাঁরা কোন রকম বৈষম্য করেন না।
“আনন্দ, তোমাকে একটা প্রশ্ন করি। মন দিয়ে শোন। একদা, যখন আমার প্রতি তুমি প্রথম নির্ভর করতে শুরু করেছিলে, তোমার কি মনে আছে যে তখন তুমি বলেছিলে আমার মধ্যে তুমি বত্রিশটি গুণ অবলোকন করেছিলে? এবার তবে আমি তোমায় প্রশ্ন করি, “কিসে তোমার দৃষ্টির চেতনা হয়েছিল? কি দেখেছিলে? কে সেই জন যে প্রীত হয়েছিল?”
আনন্দ বললেন, “সেই সময় আমার যে প্রীতিবোধ হয়েছিল, সে প্রীতিবোধ আমার চোখ দিয়ে, আর আমার মন দিয়ে। যেই মাত্র আমার চক্ষুদ্বয় দর্শণ করেছিল, তৎক্ষণাৎ আমার মন প্রসন্নতার অনুভুতি বোধ করেছিল।”
বুদ্ধ বললেন, “আনন্দ, তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে তোমার প্রসন্নতার অনুভূতি চোখে যেমন সজাত হয়েছিল, আবার মনেও সজাত হয়েছিল। আনন্দ, তোমার যদি জানা না থাকে কোথায় দর্শণের অনুভূতির উৎস আর কোথায় মনের ক্রিয়ার উৎস, তোমার পক্ষে ইহজাগতিক মোহ, আসক্তি, কলুষতাকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়।
“আনন্দ! তোমার যদি জানা না থাকে যে কোথায় তোমার আপন দৃষ্টি নামক অনুভূতিবোধের উৎস, তোমার অবস্থা হবে এক রাজার মতন। রাজার রাজত্বে দস্যুরা উপদ্রব করত, আর রাজা চাইতেন তাদের দমন করতে, কিন্তু পারতেন না; কারণ, রাজা জানতেন না যে কোথায় দস্যুরা আত্মগোপন করত। কাজেই দৃষ্টিবোধের উৎস না জানা থাকলে অজ্ঞের মতন, নিয়ন্ত্রণহীন অবস্থায় ঘুরে মরবে।
“আচ্ছা এবার তবে জিজ্ঞাসা করি? তোমার চোখ আর মনের কথা হচ্ছিল, তুমি কি জান কোথায় তাদের সেই গোপন কক্ষ? কোথায় তারা লুকিয়ে থাকে?”
আনন্দ উত্তর দিলেন, “মহাপ্রভু! জীবনের তাবৎ দশ অবস্থায়, যেখানে আর যাই হোক, চোখ থাকে আননমণ্ডলের সুমুখ ভাগে, আর আর মন লুকিয়ে থাকে শরীরের অভ্যন্তরে!”
বুদ্ধদেব আনন্দকে থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, “এই যে সভাগৃহে বসে উন্মুক্ত কক্ষ দিয়ে বাইরের দিকে দেখছ আনন্দ, সর্বপ্রথমে কি দেখছ?”
আনন্দ: “প্রথমেই আমি আমার প্রভুকে দেখতে পাচ্ছি, তৎপরে দেখি সমবেত মান্যবর শ্রোতৃবৃন্দ, সেই সব দেখার পরই দেখতে পাচ্ছি উদ্যান ও বৃক্ষরাজি।”
বুদ্ধদেব: “এই যে বাইরের দিকে তাকিয়ে নানান রকমের দৃশ্য অবলোকন করছ, এক থেকে আরেক কে আলাদা করে দেখতে পাচ্ছ, কি কারণে এই বোধ জাগছে?”
আনন্দ: “সভাগৃহের দ্বারটি যে উন্মুক্ত।”
বুদ্ধদেব: “দৃষ্টি যদি সত্যিই তোমার শরীরের অভ্যন্তরে থাকত আনন্দ, একই রকম ভাবে তুমি সর্বাগ্রে শরীরের অভ্যন্তরকে দেখতে পেতে, আর সেটা দেখার পরই তুমি বাইরের জগৎকে দেখতে পেতে, যেমন সভায় আমরা সবাই দেখছি। কিন্তু এমন কোন চেতন জীব নেই যে একসঙ্গে শরীরের অভ্যন্তর আর বহির্জগৎকে দেখতে পায়।”
আনন্দ প্রণাম করে বললেন, “আমার মন তবে নিশ্চয়ই আলোকবর্তিকার মত; আলো বহির্জগৎকে প্রজ্জ্বলিত করে কিন্তু আমার শরীরের অভ্যন্তরকে সে প্রজ্জ্বলিত করতে পারে না।” বুদ্ধদেব: “তাই যদি হবে, তোমার মন তোমার শরীরবোধকে বোঝে কি করে? যেমন, এই যে দৃশ্য দেখছ, বোঝাই যাচ্ছে যে অক্ষিগোলক তোমার শরীরে, আর দেখার অনুভূতি তোমার মনে, আর এই দুজনার পারস্পরিক বোঝাপড়া নির্ভুল; তাহলে এই যে বললে মন শরীরের বাইরে, তা তো তবে অসম্ভব।”
আনন্দ: “কিন্তু প্রভু, দ্রষ্টা মন কোথাও তো থাকবে!”
বুদ্ধদেব: “কোথায় সে, আনন্দ?”
আনন্দ: “আমার দ্রষ্টা মন নিশ্চয়ই আমার চোখ ঢেকে রাখা স্ফটিকের পাত্রের মত।
বুদ্ধদেব: “তাই যদি হবে, দৃষ্টি যদি দ্রষ্টার কেবল মনে থাকে, তবে তো তোমার চোখ তুমি আয়নার সাহায্য ছাড়াই দেখতে পেতে।”
আনন্দ: “ভগবন, তাহলে হয়ত আমার দ্রষ্টা মন আমার দুই চোখ আর দ্রষ্টব্য বস্তুর মাঝামাঝি কোথাও আছে।
বুদ্ধদেব: “আনন্দ, এখন তোমার মনে হচ্ছে মন কোন কিছুর মাঝখানে রয়েছে। দ্রষ্টা মন কেমন করে চোখ ও দ্রষ্টব্য বস্তুর মাঝামাঝি অবস্থান করবে, যখন দ্রষ্টা মন ও চোখ যেন একে অপরের সঙ্গে একাত্ম হয়ে আছে?”
আনন্দ: “কিছুকাল আগে, ভগবন যখন মৌদগল্যায়ণ, সুভূতি, পূর্ণ, ও সারিপুত্র — এই চার মহাজ্ঞানীর সঙ্গে ধর্মালাপ করছিলেন, আপনাদের বাক্যালাপ আমি কান পেতে শুনেছিলাম। ভগবন বলেছিলেন, চেতন, দ্রষ্টা, বিজ্ঞানী মনের কোন বিশেষ স্থানে অস্তিত্ব নেই, না সে অন্তরে অধিষ্ঠিত, না সে বাইরে অবস্থিত।”
বুদ্ধদেব: “আনন্দ! বিজ্ঞানী, দ্রষ্টা, চেতন মনের স্থির অবস্থান কোথাও নেই; না ইহজগতে, না উন্মুক্ত প্রান্তরে, না জলে, না স্থলে, না সে পক্ষ বিস্তার করে উড্ডীয়মান, না সে চলমান, সে কোথাও নেই।”
এই কথা শুনে সভামধ্যে আনন্দ তাঁর আসন থেকে উথ্থান করলেন। তাঁর গলবস্ত্র সামলে, ডান জানুতে ভর করে নতজানু হলেন, দুই হাত জোড় করলেন, শ্রদ্ধাভরে বুদ্ধদেবকে প্রণাম করে বললেন, “ভগবন! যদিও আপন অধ্যয়নবলে আমি বহু জ্ঞান লাভ করেছি, তথাপি মনের কলুষতা ও আশ্লেষ হতে আমি মুক্ত হতে পারিনি। তাই বারবণিতাগৃহের মায়াজাল আমি ছিন্ন করতে অক্ষম হয়েছি। আমার মন বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিল, আমি কলুষতার পারাবারে নিমজ্জিত হতে চলেছিলাম। এখন আমার দৃষ্টি উন্মুক্ত হয়েছে, আমি বুঝেছি আমার সঙ্গে যা হয়েছে আমার অজ্ঞানতাবশত সৎ চিৎ-এর সম্যক উপলব্ধি হয়নি তাই হয়েছে। হে প্রভু, আমাকে ক্ষমা ও করুণা করুন। আমাকে যথার্থ পারমার্থিক পথ দেখান। সেই পথ, যে পথে আমার অতীন্দ্রিয় ধ্যানের উপলব্ধি হবে, যে পথে আমার আত্মনিয়ন্ত্রণ হবে, যাতে আমি কুপ্রলোভন হতে, জন্ম জন্মান্তরের বেদনা হতে মুক্ত হতে পারি।”
বুদ্ধদেব তখন সভাকে সম্বোধন করে বললেন, “অনাদি অনন্তকাল ধরে, জন্ম-জন্মান্তরে, সকল চেতন প্রাণী নানান রকম মায়ার জড়িয়ে পড়েছে; প্রাণীকূল আপন আপন কর্মহেতু তাদের স্বভাব অনুযায়ী আবদ্ধ: যেন দর্ভিকার বীজপত্র — তাদের উন্মোচন করা মাত্রেই তিনটি বীজ একত্রিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে।
“দুটি মূল তত্ত্ব উপলব্ধি না করতে পারার কারণে ধার্মিকগণ পরম জ্ঞান অর্জন করতে অক্ষম হন। একই কারণে কারো কারো পূর্ণ অর্হতত্ব অপূর্ণ থেকে যায়, আবার কারো কারো নবীন সাধুর ন্যায় অর্ধ সত্যের উপলব্ধি হয়; আবার কেউ কেউ বিভ্রান্ত হয়ে অসৎ চর্চায় নিবেশিত হয়ে পড়ে। এ যেন পাথর আর বালুকারাশি দ্বারা সুখাদ্য রন্ধনের ব্যর্থ প্রয়াস: অগণিত কল্প ধরে চেষ্টা করে গেলেও সে চেষ্টা ব্যর্থ হবে।
“এই দুই তত্ত্ব হল: “এক, অনাদি অনন্তকাল ধরে চলে আসা জন্ম জন্মান্তর পুনর্জন্মের মূল কারণ অনুধাবন। এই তত্ত্ব অনুধাবন করলে সেখান থেকে সচেতন প্রাণীসমূহের মনের ভিন্নতা বোঝা যায় । উপলব্ধি হয় যে যুগ যুগ ধরে সকল চেতন প্রাণী তাদের সীমিত, কলুষিত ও বিপন্ন মনকেই সৎ চিৎ বলে ভ্রম করে।
“দুই, বোধি ও নির্বাণের অভিন্নতার যে কারণ অনাদি অনন্তকাল ধরে বিরাজমান, তাকে উপলব্ধি করা। এই তত্ত্বকে আপন অন্তরে গ্রহণ করে তাকে সম্যক ভাবে আপন অন্তরের আলোকে উপলব্ধি করে, সেই একত্রতার সারমর্মকে নানাভাবে আবিষ্কার করা, তাকে উপলব্ধি করা, তাকে আপন অন্তরে বিকশিত করা। তোমরা যে সেই সারতত্ত্ব বিস্মৃত হও তার কারণ তোমরা তোমাদের অন্তরের শুদ্ধ চেতন মনকেই বিস্মৃত হও, সারাদিনের কর্মব্যস্ততার মধ্যে সে যে অন্তরে আছে, সেই ব্যপারটাকেই তোমরা ভুলে যাও। আর তাই, আনন্দ, তুমি ও আর সকল চেতন প্রাণী অজ্ঞানতাবশত দুঃখে ও অস্তিত্বের নানান অবস্থায় নিপতিত হও।”
এবার তথাগত মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে আনন্দকে জিজ্ঞাসা করলেন, “আনন্দ, আমার মুষ্টিবদ্ধ হাতের দিকে তাকাও। আমার এই মুষ্টিবদ্ধ হাত দর্শণে তোমার আপন সৎ চিৎ-এর কি উপলব্ধি হচ্ছে?”
আনন্দ উত্তর দিলেন, “এই যে চিন্তামগ্ন, যুক্তিবাদী সত্তা, যে সত্তা আমাকে আপনার জ্যোতির্ময় উত্তোলিত মুষ্টিবদ্ধ হস্ত দর্শণ করতে সক্ষম করছে, একেই আমি “আমার মন” বলি।”
বুদ্ধদেব আনন্দকে ধমক দিয়ে বললেন, “আনন্দ, তোমার সত্তাকেই তোমার মন বলে বসলে, এ যে একেবারেই ভুল।”
আনন্দ হাত জোড় করে উঠে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে বললেন, “কেন প্রভু, আমার সত্তা যদি আমার মন নাই হবে, তবে আর কে আমার মন হতে পারে? আমিই আমার মন! আমি যদি আমার মন-বোধ-উপলব্ধি-চেতন পরিত্যাগ করি, তাহলে তো আমি বা আমার মন বলে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না!”
এই কথা শুনে পরমজন স্নেহভরে আনন্দের মাথায় তাঁর হাত রাখলেন ও বললেন, “আচ্ছা এই যে আমি আমার হাতের মুষ্টি এবার সরিয়ে নিলাম, এর যে দৃশ্য তা তো তোমার চিন্তা ও যুক্তি থেকে এক্ষণে অদৃশ্য হয়েছে, তাতে কি তোমার মনও শূন্যে বিলীন হয়ে গেল, নাকি অসম্ভব একটা কিছুতে পর্যবসিত হল, যেমন কচ্ছপের লোম বা শশকের শৃঙ্গের মতন কিছু একটা হয়ে গেল?”
“যেহেতু তোমার মন সেই সব দৃশ্যের স্মৃতি আর আমার মুষ্টিবদ্ধ হাত দেখার চেতনা, এই দুই উপলব্ধির তফাৎ করেই চলেছে, অতএব সে তো শূন্যে বিলীন হয়ে যায়নি।
“আনন্দ ও সমবেত শিষ্যগণ! এই যে আনন্দ বলছে যে সে নিজেই তার মন, এর পরিপ্রেক্ষিতে বলি, আমি তোমাদের সর্বদা এই শিক্ষা দিয়ে এসেছি যে প্রপঞ্চময় জগৎ কেবল তন্মাত্র মনের বহিঃপ্রকাশমাত্র, তার বেশী কিছু নয়। তোমরা যাকে সত্তা বল, এও তাই, তন্মাত্র মনের বহিঃপ্রকাশ বই কিছু নয়।
“আমরা যদি সমগ্র মহাজগতের সকল বস্তুনিচয়ের উৎপত্তি পরীক্ষা করে দেখি, দেখব যে সকলই এক আদি সারাৎসারের বহিঃপ্রকাশ । কি অতি ক্ষুদ্র তৃণ, কি কোন সূত্রের গ্রন্থি, সমস্ত কিছু। বিবচনা করে দেখলে দেখবে সমস্ত কিছুর আদিতে সেই এক সারাৎসার।
“সমুদ্রে যে তরঙ্গ ওঠে, তার সারাৎসার সমুদ্র। এই রকম করে ভাবলে, মনের যে চিন্তা, তার সারাৎসার, মন।
“এই যে আমাদের সত্তা, সকল বস্তু, আপন সত্তার ক্রমাগত পরিবর্তনশীলতা, এর কোন কিছুই নিত্য নয়। সমস্ত বস্তু আর চিন্তার মতন, এরা সব তরঙ্গ; এরা যেইমাত্র বিলীন হয়, পুনরায় তোমাদের জিজ্ঞাসা করি, যেইমাত্র এরা বিলীন হয়, অমনি তোমার মনও কি শূন্যে বিলীন হয়, নাকি অলীকপ্রাপ্ত হয়, যেন কূর্মের পৃষ্ঠদেশে রোম, বা শশকের মস্তকে শৃঙ্গের ন্যায় অবাস্তব হয়ে যায়?
“স্মৃতিও যদি এদের সঙ্গেই বিলীন হত, তবে তো আর কিছুরই অস্তিত্ব থাকত না, কোন চেতন প্রাণের প্রশ্নই উঠত না।
“স্মৃতি শূন্যে বিলীন হয় না, কারণ সে প্রপঞ্চময় জগতের অতীত; কারণ কোনটা সত্তা কোনটা সত্তা নয়, সে এই সব ভেদাভেদের সে উর্দ্ধে! সে অভেদ ।
“মন যেইমাত্র বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে বিভেদ নির্ণয় করতে শুরু করে, মহাবিশ্বজগৎ থেকে আরম্ভ করে ক্ষদ্রাতিক্ষুদ্র ধুলিকণা, যাকে সূর্যালোক ভিন্ন প্রত্যক্ষ করা যায় না, অমনি তাদের অস্তিত্ববোধ হয়, যেমন সমুদ্রে তরঙ্গ ওঠে।
“এই যে দৃশ্যমান জগৎ তাকে আমরা সর্বব্যাপী মহামানস-সারাৎসার-সমুদ্রে তরঙ্গের মতন দেখি; আমরা জানি যে এই তরঙ্গ অস্তিত্বের ত্রিগুণের সমন্বয় — এক সে তন্মাত্র ও ক্ষণস্থায়ী; দুই, সে চঞ্চল, অশান্ত, দুঃখী, বিব্রত, সদা সঞ্চরমাণ; তিন, অনস্তিত্ব, তার প্রকৃতপক্ষে কোন অস্তিত্ব নেই: তরঙ্গ যেমন হাওয়ার কারণে জলের রূপের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। একই রকম ভাবে প্রপঞ্চময় বিশ্ব যাকে দেখতে পাই সে অজ্ঞানতার কারণে জাত মানস সারাৎসারের বহিঃপ্রকাশ মাত্র।
“তাই, আনন্দ, আমার উত্তোলিত মুষ্টি দর্শণে ‘যে’ তোমাকে তোমার মানস অস্তিত্বের সারাৎসারের সন্ধান দিয়েছে, সে আমার মুষ্টি দর্শণে তোমার বিভেদ-সৃষ্টিকারী মনের বিভিন্নতা দর্শণের হ্যাঁ বা না কোনটাই নয়; দুটোই কেবল তরঙ্গ বই কিছু নয়। সকল দৃশ্যমানতার উৎস তোমার সারাৎসার মন, সমুদ্র যেমন তরঙ্গের উৎস।
“যতদিন পর্যন্ত তুমি এই নানান রকম ভেদাভেদ সৃষ্টিকারী ইন্দ্রিয়-মস্তিষ্ককেই সারাৎসার মন বলে ভুল করবে, যতকাল তুমি এই বস্তুতে বস্তুতে বিভেদ সৃষ্টিকারী অনিত্য মনের চিন্তাভাবনাকে আঁকড়ে ধরে রাখবে, যতদিন তুমি মায়াময় ছলনাকে সত্য বলে গ্রহণ করবে, ততদিন জাগতিক মোহ থেকে তোমার মুক্তি হবে না; চিরকাল এই দুঃখচক্রের দাসত্বে বাঁধা পড়ে থাকবে। এই নশ্বর, চঞ্চল, অশুভ, জগৎ সংসার, যা সত্যের মহোজ্জ্বল জ্যোতিষ্কে কলঙ্কমাত্র, তার মায়াজাল থেকে তোমার নিস্তার নেই।
আনন্দ কাঁদছেন।
আনন্দ তাঁর শিক্ষার ও বিরক্তিপ্রকাশের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করলেন, ও স্বীকার করলেন, এই দুটোই তাঁর কাছে মস্ত বাধা।
বুদ্ধদেব পুনরায় তাঁর মুষ্টিবদ্ধ হাত উজ্জ্বল আলোয় আনন্দের সামনে তুলে ধরলেন,
“বলত আনন্দ, কি উপায়ে আমার মুষ্টিবদ্ধ হাতের ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ পাচ্ছে?”
আনন্দ: “আলো উজ্জ্বল, তাই তাকে আমার চোখ দিয়ে দেখি, ও আমার মন দিয়ে এ যে উজ্জ্বল, তা বুঝি।”
বুদ্ধদেব: “তোমার দৃষ্টি কি উজ্জ্বলতার ওপর নির্ভর করে?”
আনন্দ: “উজ্জ্বলতা না থাকলে যে কিছুই দেখতে পাব না।”
বুদ্ধদেব: “মানুষ যখন অন্ধ হয়ে যায়, তখন অন্ধ মানুষ অন্ধকার ভিন্ন কিছুই দেখতে পায় না। এ তার অন্ধত্বের ধারণা, তাতে তার দৃষ্টির ধারণার কোন ক্ষয় হয় নি। অন্ধকার কক্ষে চক্ষুষ্মান মানুষ যা দেখে সেও তাই দেখতে পায়। চোখ বন্ধ কর আনন্দ, তুমি অন্ধকার বাদে আর কি দেখতে পাচ্ছ?” আনন্দ স্বীকার করলেন যে তিনি কেবল অন্ধকারই দেখছেন । বুদ্ধদেব: “অন্ধ মানুষ যদি হঠাৎ দৃষ্টি ফিরে পান, সে যেন হবে হঠাৎ করে অন্ধকার কক্ষে একটি আলোর শিখার প্রজ্জ্বলন। আমরা হয়ত তখন বলব যে মানুষ প্রদীপের সাহায্যে দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু দৃষ্টি, দৃষ্টি ব্যাপারটার বোধ, তা কিন্তু উজ্জ্বলতা, কি অন্ধকার, প্রদীপ কি চোখ, এদের কারোর ওপর নির্ভর করে না। কারণ দেখা, দেখতে পাওয়া, দৃষ্টি, এ তোমার সারাৎসার,আদি, মহতী মনে তার উদয়, তার সৃষ্টি। সারাৎসার সেই মন সমস্ত কিছুর অতীত — সে সর্বত্র বিরাজমান — কার্য কারণ, সবেতে সে বিদ্যমান — ঔজ্জ্বল্য, অন্ধকার, চোখ, প্রদীপ; আবার সে তাবৎ অবস্থা থেকে মুক্ত, যখন যেমন পরিস্থিতির উদয় হয়, দৃষ্টি তাতেই সংবেদনশীল। সমুদ্রের মতন । সমুদ্র তার তরঙ্গের অতীত, অথচ প্রতিটি তরঙ্গে সে বিদ্যমান, যখন যেমন তরঙ্গের উদয় হয়, সমুদ্রও সেইমত সাড়া দেয়।
“বলতে গেলে, তোমার মনের উজ্জ্বলতার ধারণা, বা তোমার চোখ, এরা কেউই আমার উদ্যত মুষ্টি প্রত্যক্ষ করে নি।”
আনন্দ হতভম্ব হয়ে বসে রইলেন। ভাবলেন বুদ্ধদেব যদি স্নেহভরে আরেকটু সরল করে বুঝিয়ে বলেন! তিনি শুদ্ধচিত্তে, আরো কিছু শুনতে পাবার অপেক্ষায় উৎসুক হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। মহৎ জন, পরম করুণায় আনন্দের মাথায় হাত রাখলেন। রেখে বললেন, “বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি না হলে যে সচেতন প্রাণীগণ সম্যক আলোকপ্রাপ্ত হয় না, তার কারণ, তারা কি প্রপঞ্চময় জগৎ, কি বস্তু, এ সবের সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণাবশত বিপথে যায়। তারা সবাই তাদের গভীর স্বপ্নে বিভোর। তারা তাদের সৎ চিৎ-এর, সারাৎসার মানসের যে উজ্জ্বল সার্বিক শূন্যতা, যে মানস সর্বত্রগামী, তার যে বাস্তবতা, তাতে আর জেগে উঠতে পারে না। তারা জানেই না যে যা কিছু দেখে তার সব কিছুরই উৎস মন।
“মানসের চেয়ে তারা স্বপ্নেই বরং নিবেশিত।
“সারাৎসার মানস যেন একটি উন্মুক্ত প্রান্তর। সে অনাদি, সে অনন্ত, সে স্থির, অচঞ্চল। ধুলিকণা যেমন খোলা আকাশের নীচে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে এই আছে এই নেই, সেই রকম আমাদের অস্তিত্বের স্বপ্ন।
“সারাৎসার মানস যেন একটা সরাইখানা। কিন্তু আমাদের অস্তিত্বের স্বপ্ন যেন সেই সরাইখানার একরাতের ভবঘুরে পর্যটক; রাত কাটিয়ে তাকে আবার চলে যেতে হবে, চরৈবেতি। বুদ্ধদেব হাত তুললেন, তারপর একবার মুঠো খুললেন, তারপর আবার মুঠো বন্ধ করলেন। করে আনন্দকে জিজ্ঞাসা করলেন, “কে স্থাবর, কেই বা জঙ্গম, আনন্দ?” আনন্দ দেখলেন মহৎ জনের মুষ্টিবদ্ধ হাত একবার খুলল, একবার বন্ধ হল, তাঁর নিজের ‘দৃষ্টি’ তে কোন চাঞ্চল্য ছিল না। তিনি বললেন, “ভগবন, আপনার আঙুলগুলোতেই গতি, আমার চোখের দৃষ্টিতে তো কোন গতি নেই।” “আনন্দ”, বুদ্ধদেব বললেন, “যা চলমান, জঙ্গম, পরিবর্তনীয়, আর যা স্থাবর, অপরিবর্তনীয়, এই দুইয়ের চরিত্রগত পার্থক্য কি তুমি বুঝতে পারলে না? শরীর ক্রমশ চলমান, চঞ্চল, পরিবর্তিত হতে থাকে, মন নয়। মন স্থির।
“কেন তুমি বারবার শরীর-মন উভয়ের গতির কথা বলে চলেছ? কেন তোমার মনের চিন্তা ভাবনাকে একবার উঠতে দিচ্ছ, একবার পড়তে দিচ্ছ, তোমার শরীর কেন তোমার মনকে নিয়ন্ত্রণ করে, কেন তোমার মানসচেতনা তোমার শরীরকে নিয়ন্ত্রণ করে না?”
“কেন ইন্দ্রিয়ের ছলনায় তোমার স্বরূপ মানসকে উপলব্ধি করতে পারছ না? করতে পারছ না বলে অজ্ঞানতার নীতিবলে যে রাস্তায় চলা উচিৎ তার উল্টোরাস্তায় চলছ কেবল, যে পথে শুধুই পদে পদে বিহ্বলতা, যাতনা?
“মানুষ যেমনই তার সৎ চিৎ কে বিস্মৃত হয়, তখনই সে অন্তহীন গভীর মনের একেবারে উপরভাগে যে ছোট ছোট তরঙ্গ উথ্থিত হয়, তাকেই গভীর মন বলে ভেবে বসে, আয়নায় প্রতিফলিত বস্তুকে সে নিজের সৎ চিৎ বলে ভেবে বসে। এতে করে অনিত্য, চঞ্চলতা জাগে। জন্ম-মৃত্যু-পুনর্জন্মের অন্তহীন চক্রে পড়ে সে কেবলই যাতনা ভোগ করে।
“যা কিছু জঙ্গম, যা কিছু সচল, যা কিছু পরিবর্তনশীল, তাকে ধুলিকণার ন্যায় জ্ঞান কর। যা কিছু স্থির, অচঞ্চল, তাকে তোমার সৎ চিৎ বলে জ্ঞান কর।”
তখন, আনন্দ ও সভামধ্যে উপস্থিত আর সকলে উপলব্ধি করলেন যে, অনাদি অনন্তকাল ধরে জগতের মায়াবী প্রতিফলন দেখতে দেখতে তাঁরা তাঁদের আপন স্বরূপকে বিস্মৃত হয়েছেন, সেই স্বরূপকে উপেক্ষা করে এসেছেন। এ জগৎ কেবলি মানস । যেন একটি ছোট শিশু মাতৃস্তন খুঁজে পেয়েছে, এমনি তাঁদের বোধ হল, তাঁরা অন্তরে বাহিরে প্রশান্তি অনুভব করলেন। তাঁরা ভগবার তথাগতের কাছে প্রার্থনা করলেন তিনি যেন তাঁদের শিক্ষা দেন শরীর ও মন, সৎ-অসৎ, মৃত্যু-পুনর্জন্মের প্রকাশ ও আমাদের অন্তর্নিহিত অজর অমর অজাত চরিত্রের কি পার্থক্য।
মহারাজ প্রসেনজিৎ উঠে দাঁড়িয়ে বুদ্ধদেবকে অনুরোধ করলেন এমন কিছু শিক্ষা দান করতে যাতে না-মৃত্যু না-পুনর্জন্মের সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। যাতে তিনি মৃত্যু-পুনর্জন্মের কালচক্র থেকে কি করে নিস্তার পাওয়া যায় তা বুঝতে পারেন। বুদ্ধদেব তাঁকে তিনি যুবাবয়সে যেমন দেখতে ছিলেন সে তুলনায় এখন তিনি কেমন দেখতে সে কথা বলতে বললেন। মহারাজ বললেন, “সে আমি কেমন করে বলব? আমি কেমন করে আমার যুবা বয়স আর এই বয়সের তুলনা করব?” এই বলে বছরে বছরে দিনে দিনে যে ক্ষয়ে যাচ্ছেন সেইসব বলতে লাগলেন। “হ্যাঁ, দিনে দিনে, এই করে করে একদিন সব শেষ হয়ে যাবে।”
তখন বুদ্ধদেব মহারাজ প্রসেনজিৎকে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি প্রথম যখন গঙ্গানদী দেখেছিলেন তখন কত বছর বয়স ছিল; মহারাজ প্রসেনজিৎ বললেন, তিন বছর; তারপর যখন দ্বিতীয়বার গঙ্গানদী দেখলেন তখন কত বছর বয়স ছিল, মহারাজ বললেন তের বছর; এখন তাঁর কত বছর বয়স, মহারাজ উত্তর দিলেন, বাষট্টি বছর; বুদ্ধদেব প্রশ্ন করলেন, গঙ্গানদী এই যে এত বছর ধরে দেখে এলেন, সেই দেখার কি পরিবর্তন হয়েছে। মহারাজ প্রসেনজিৎ উত্তর দিলেন, “আজকাল চোখে তো তেমন ভাল দেখতে পাই না, কিন্তু আগেও যা দেখেছি, গঙ্গাকে এখনো তেমনই দেখি।” বুদ্ধদেব তখন বললেন, “মহারাজ! যুবাবয়স থেকে আজ অবধি আপনার অবয়বে যে পরিবর্তন হয়েছে তাতে আপনি বিষন্ন বোধ করছেন — আপনার চুলে পাক ধরেছে, আপনার আননমণ্ডলে ত্বক কুঞ্চিত হয়েছে, রক্ত চলাচল কমে আসছে, কিন্তু আপনি বললেন, আপনার দৃষ্টির যে চেতনা, তা যুবাবয়সে যেমন ছিল, আজও তেমনই আছে। বলুন মহারাজ, দৃষ্টির চেতনার কি যুবকাল বা বার্ধক্য বলে কিছু আছে?”
মহারাজ উত্তর দিলেন, “না, ভগবন”।
তখন বুদ্ধদেব বললেন, “মহারাজ! যদিও আপনার মুখমণ্ডল কুঞ্চিত হয়েছে, আপনার দৃষ্টির চেতনায় কোন কুঞ্চন দেখা দেয় নি, তাতে বয়সের কোন ছাপ পড়েনি। এ থেকে বোঝা যায় কুঞ্চিত হওয়া মানে পরিবর্তনশীলতা, কুঞ্চিত না হওয়া মানে অপরিবর্তনশীলতা। যা পরিবর্তনশীল তা নশ্বর। তার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। যা অপরিবর্তনশীল, তা মৃত্যু-পুনর্জন্ম হতে মুক্ত।”
তথাগতের মুখে এই সুপ্রাচীন বাণী শ্রবণ করে সভায় যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা পরম হর্ষ অনুভব করলেন। তাঁদের অশ্রুতপূর্ব সত্যের উপলব্ধি হল।
তারপর আনন্দ জানতে চাইলেন, বৃহৎ মনের উপলব্ধি যখন মৃত্যু ও পুনর্জন্ম থেকে মুক্ত, তবুও কেন মানুষ তাদের মনের স্বরূপ বিস্মৃত হয়, কেনই বা তারা “বিপরীতমুখী বিহ্বলতায়”, অজ্ঞানতার তত্ত্বে কাজ কর্ম করে। বুদ্ধদেব তাঁর বাহু প্রসারিত করলেন, করে তাঁর আঙুলগুলো নীচের দিকে নির্দেশ করে অদ্ভুত কি এক মুদ্রা প্রদর্শন করলেন। করে আনন্দকে প্রশ্ন করলেন, “আনন্দ, এই ভঙ্গিমাকে যদি নিম্নমুখী বলি, কাকে তুমি উর্দ্ধমুখী বলবে?” “ভগবন, আঙুল উপরের দিকে তুলে ধরলে তাকে উর্দ্ধমুখী বলব।” বুদ্ধদেব সহসা হাত ঘুরিয়ে আনন্দকে বললেন, “হাত ঘুরিয়ে আঙুল উপরের দিকে কি নীচের দিকে নির্দেশ করলে যদি অবস্থানের ব্যাখ্যা করা যায়, কি উর্দ্ধমুখী, কি নিম্নমুখী, যে যেভাবে দেখে সেইভাবে, তবে জেনে রেখো যে সার্বজনীন তন্মাত্র মন, যে সর্বত্র সদাসর্বদা সব হয়ে আছে, যে তথাগতের গর্ভ, যে পরিপূর্ণ ধর্মকায়া, তাকেও অবস্থাভেদে বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে উপলব্ধি করা যায়; অস্তিত্বের অতীত নির্বাণকল্পে, তথাগতের পরম বোধিরূপে (সমুজ্জ্বল, পরম, শূন্য, অমর), অথবা সংসাররূপে, ইহজাগতিক, অসৎ, মরজগৎ, তমসাচ্ছন্ন, দুঃখময়, অজ্ঞানতার মায়ায় আচ্ছন্ন বিভেদকারী মস্তিষ্কগত মনরূপে, “বিপরীতমুখী অবস্থান”।
আনন্দ ও অন্যান্য সভাস্থিত ভক্তগণ এই কথা শুনে অবাক হয়ে বুদ্ধদেবের দিকে অপলক নেত্রে চেয়ে রইলেন। মনের বিপরীতগত অবস্থান বলতে বুদ্ধদেব কি বোঝাতে চাইছেন? তাঁরা এই যে বুদ্ধদেবকে নিজের চোখে দর্শণ করছেন, পরম শূন্য কিছু তো দেখছেন না, এও তো তাহলে মনের “বিপরীতমুখী অবস্থানের” কারণে!
বুদ্ধদেবের হৃদয়ে আনন্দ ও অন্যান্য ভক্তগণের প্রতি অপার করুণার সঞ্চার হল। তিনি তখন তাঁদের বুঝিয়ে বললেন, “হে মোর শিষ্যগণ! আমি কি বার বার তোমাদের এই শিক্ষা দিচ্ছি না যে মনের ধারণা, ও ক্রমাগত পরিবর্তনশীল প্রপঞ্চময় এই জগতের সমস্তকিছু কার্যকারণ প্রসূত, মনের নানারকম ধারণা, সমস্তই মনের বহিঃপ্রকাশ, তোমাদের শরীর ও মন, সে সকলই পরম, তন্মাত্র, সর্বগামী, আনন্দময়, আলোকিত, রহস্যময় তন্মাত্র সার মানসের বহিঃপ্রকাশ বই আর কিছু নয়।
“স্বপ্নের মত, সমস্ত কিছু তোমাদের মনে ঘটে চলেছে।
“যে মুহূর্তে স্বপ্ন দেখা শেষ হয়ে তোমরা জেগে উঠবে, তোমাদের মন আদিম শূন্যতার পরমতায় ফিরে যাবে।
“সত্যি বলতে কি, তোমাদের মন এখনই সেই পরম, নিষ্কলুষ শূন্যতায় প্রত্যাবর্তন করেছে, এই জগৎ অতি সাধারণ মায়াময় প্রতিচ্ছায়া বই আর কিছু নয়।
“তোমরা কি করে এত সহজে এই অপূর্ব, পূর্ণালোকিত, সম্যকরূপে পবিত্র যে মন, তাকে ভুলে যাও?”
এই বলে বুদ্ধদেব অল্প কথায় বিশ্বের জন্মরহস্য ব্যাখ্যা করলেন, “উন্মুক্ত স্থান অদৃশ্য এক নিষ্প্রভতা বই কিছু তো নয়। স্থানের এই অদৃশ্য নিষ্প্রভতা যখন অন্ধকারের সঙ্গে মিশে যায়, তখন অবয়বের মত দেখায়। অবয়বের এই যে অনুভূতি, এই অনুভূতি সে কালক্রমে মায়াময় ও বিশ্ব-প্রপঞ্চের একটা যদৃচ্ছ ধারণায় পরিণত হয়। এইভাবে প্রপঞ্চময় জগতের একটা মিথ্যা কাল্পনিক ধারণার শারীর চেতনার, উদ্ভব হয়। “অতএব, মনের অভ্যন্তরে, স্ব-এর মস্তিষ্ক মন দেখলে, এই যে এতসব কার্য-কারণ তালগোল পাকিয়ে রয়েছে, তারা আবার নানান রকমের দল বেধে আছে, এরা যখন বিশ্বের প্রক্ষিপ্ত বিষয়ের সঙ্গে জুড়ে যায়, সেখান থেকে ভীতি আর আকাঙ্খা জেগে ওঠে। মনের স্বাভাবিক অনড় যে প্রশান্তি, ভীতি আর আকাঙ্খা তাকে নষ্ট করে দেয়, তা নষ্ট হবার পর, হয় আবেগ নয় প্রবল ভীতি, হয় মর্ষ, নয় ক্রোধের জন্ম হয়। আর তোমরা সবাই এই গোলমেলে আত্ম-সচেতনতার ধারণাকে নিজের মনের স্বরূপ বলে ধরে নিচ্ছ। “যেইমাত্র একে তোমার মনের স্বরূপ বলে গ্রহণ করবে, তুমি বিহ্বল হয়ে পড়বে, মনে করবে যে মন শরীরেরই অংশ, ভাববে যে আর সমস্ত বহির্জগতের যা কিছু, পর্বত, নদী, উন্মুক্ত স্থান, গোটা বিশ্ব তোমার শরীরের বাইরে। এতে বিস্ময়ের কি আছে?
“বিস্ময়ের কিছু আছে কি যে, এই প্রপঞ্ময় বিশ্ব নিয়ে যা মিথ্যা ধারণা করলে, তার যে অস্তিত্ব তোমার পরম আলোকিত তন্মাত্র মনে, সেটুকুও উপলব্ধি করলে না?
“এ কেমন ব্যাপার জান? তোমরা অনন্ত শান্ত মহাসমুদ্রের জল ছেড়ে একটা ছোট্ট ঢেউকে আঁকড়ে ধরলে, এই ঢেউটাকে শুধু আঁকড়ে ধরলে শুধু তাই নয়, তাকেই অনন্তকোটি সমুদ্রের জলের সামগ্রিক রূপ বলে মেনে নিলে। তারপর হতবিহ্বল হয়ে গেলে।
আমার আঙুল ওপরেই ওঠাই বা নীচেই নামাই, তাতে তো আমার হাতের অবস্থানের কোন পরিবর্তন হয় না। সেই রকম, তুমি মনের স্বরূপ ভুলে যাও বা না যাও, তাতে তো মনের সৎ চেতনা/ধারণার কোন পরিবর্তন হয় না। কিন্তু জগৎ একটা তফাৎ নির্ণয় করে ফেলে — বলে যে এই হাত ওপরে উঠল, এই হাত নীচে নামল, এই মনের অবস্থা নির্বাণের পরমতা, আবার এই সে সংসারের পাঁকে পড়েছে। পরম মন যেহেতু কোন প্রকার ধারণার উর্দ্ধে, যারা এই দ্বিধাদ্বন্দে ভোগে তাদের করুণা ছাড়া কিই বা করা যেতে পারে?”
আনন্দ, বুঝলেন যে তাঁর এই নিয়ত পরিবর্তনশীল ভেদবুদ্ধিকারী, মস্তিষ্কগত মনের মূলে রয়েছে এক অবিচল পরম তন্মাত্রিক মন।। তিনি জানতে চাইলেন যে, এই যে মন দিয়ে তিনি তাঁর গুরুর পরম মনের শিক্ষাকে নিজের মত করে বুঝছেন, ভেদাভেদ করছেন, সেই মন আর পরম মন একই কিনা। বুদ্ধদেব উত্তর দিলেন, “আনন্দ! শিক্ষা দিতে গিয়ে যখন একবার আঙুল তুলে চাঁদের দিকে দেখালাম, তখন ভাবলে আমার আঙুলই বুঝি চাঁদ। সেই, যা আমার শিক্ষা তোমাকে বুঝতে সাহায্য করেছে, তাকে যদি তোমার নিজের মন বলে ভাব, তাহলে, সে যখন এই শিক্ষাকে একপাশে সরিয়ে রাখবে, সেই মন, তখনো সে তার ভেদবুদ্ধিকে রেখে দেবে। তা তো সে করে না।
“এ যেন এক পথিক। পথিক সরাইখানায় এসেছে এক রাত থাকবে, চীরকাল সেখানে সে রইবে না। কিন্তু সরাইখানার যে মালিক, সে চিরকাল সেখানেই থাকবে, আর কোথাও চলে যাবে না। এও তাই। বিভেদ-দর্শণকারী মস্তিষ্কগত মন যদি তোমার পরম মনই হবে, তবে সে অনিত্য, সে অপরিবর্তনীয়। দেখ যেই আমার কন্ঠস্বর থেমে যাবে, অমনি তারও এই এক কে আরেকটি থেকে পৃথক করে দেখার ব্যাপারটা থেমে যাবে, তাহলে সে আর পরম মন হল কি করে? “তোমার মস্তিষ্ক-মন, যে কিনা মহাসমুদ্রে তরঙ্গ, আর অন্তর্নিহিত মহামানস, যে কিনা সমুদ্র স্বয়ং, তাদের উভয়েরই একটি একমেবাদ্বিতীয়ম রূপ আছে, একটাই স্বরূপ।”
আনন্দ বললেন, “প্রভু, যদি আমার বিভেদ দর্শণকারী মস্তিষ্ক-মন আর তার যে অন্তর্নিহিত মহামানস তার একই উৎস হবে, তবে কেন, সেই পরম মন যা সমুদ্রসদৃশ, যাকে ভগবন আমার মস্তিষ্ক-মনের সঙ্গে এক বলে মনে করেন, কেন তা তার আদিরূপে ফিরে যায় না?” এই বলেই আনন্দ উপলব্ধি করলেন যে, তিনি এমন এক আদিচেতনার কথা বলছেন যার কোথাও “ফিরে” যাবার নেই।
তখন বুদ্ধদেব যে শিক্ষাদান করলেন সেই শিক্ষা গ্রহণ করে সমবেত ভক্তবৃন্দ তাঁদের আপনাপন ভ্রান্ত অবলোকন হতে মুক্তি পেলেন। বুদ্ধদেব বললেন, “উজ্জ্বলতার ধারণা ব্যতিরেকে প্রকৃতপক্ষে উজ্জ্বলতার কোন অস্তিত্ব নেই; দিনের আলোয় দরজার দিকে তাকালে যে আলো উজ্জ্বল রূপে প্রতিভাসিত হয়, তা প্রকৃতপক্ষে কি?”
“এই আলোকোজ্জ্বলতার কারণ সূর্য নয়, যদিও সূর্য আছে বলে উন্মুক্ত স্থানে আমরা আলোর উজ্জ্বলতা প্রত্যক্ষ করি । আলোর উজ্জ্বলতার অনুভূতিকে উৎসমুখে যদি নিয়ে যাও, তবে কোথায় গিয়ে, কোন উৎসে ফিরিয়ে দেবে? সূর্যে নয় নিশ্চয়ই। তাকে ফিরিয়ে দেবে যে মন দেখেছে তার কাছে, সেইখানে।
“কেননা, তোমার উজ্জ্বলতার অনুভূতিকে যদি উৎসমুখ বলে সূর্যের কাছে ফিরিয়ে দিতে, আর তারপর একথা বলে বেড়াতে যে উজ্জ্বলতার উৎস সূর্য, তবে ভেবে দেখো সূর্যাস্তের পর যখন সূর্যের আলো আর থাকে না, তখন অন্ধকারও তোমার আর অনুভূত হবার কথা নয়। অনুভূতিবোধ যাকে বল, সে প্রকৃতপক্ষে আমাদেরই তন্মাত্র মন। সূর্যের ঔজ্জ্বল্য কি চাঁদের নিষ্প্রভতা যাকে অবলোকন করি তা যেন সেই তন্মাত্র মনের ওপরে ভাসমান তরঙ্গমাত্র। “তোমাদের কান কি আলোর উজ্জ্বলতা অনুভব করে? করে না তো। তোমাদের চোখ জানে কি স্তব্ধতা বা শব্দের অনুভূতি কেমন ? অতএব একটা ব্যাপার জেনো, আমাদের ইন্দ্রিয় যা অনুভব করে তার উৎস তন্মাত্র মনে নয়, তার উৎস সেই সব ইন্দ্রিয়েতেই।
“যেমন ধর, আনন্দ, তোমার চোখ যে সুর্যের উজ্জ্বলতা অনুভব করে, সেই উজ্জ্বলতার উৎস তন্মাত্র মনে নয়, কেননা তন্মাত্র মন আলোতেও নেই, অন্ধকারেও নেই, সে আছে তোমার চোখে, তার অস্তিত্ব তোমার চোখের নিমিত্ত।
“তুমি তো একথা জান আনন্দ, ওই যে শত সহস্র বছর ধরে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে আছে, আমরা যাকে সূর্য বলে জানি, সেই তেজোময়তা, যা তোমার চোখ, শরীর, অন্তরাত্মা অনুভব করে, তারও উৎস কিন্তু তন্মাত্র মনের পরম শূন্যতায় নয়, যা অগ্নির তাবৎ অবস্থা কি অগ্নির অবিদ্যমানতারও অতীত, সে আছে শুধু চোখে, দেহে, মনে; চোখের, দেহের, মনের জন্যই। “আনন্দ, তোমার যদি শরীর না থাকত, তোমার কাছে পৃথিবীরও কোন অস্তিত্ব থাকত না; তুমি ভেদ করে চলে যেতে। এ-ই তোমার সূর্য।
“আনন্দ, বাস্তবিক অর্থে, শরীর নেই তাই পৃথিবীরও বুঝি অস্তিত্ব নেই, একথা বলা যতটাই বাতুলতামাত্র, তেমনি শরীর আছে, তাই পৃথিবীর অস্তিত্ব আছে, এই কথা বলাও একই রকম অর্থহীন। কারণ সর্বত্র একই দর্শণ, সর্বত্রই সেই একই শূন্যতা। এ-ই তোমার সূর্য।
বুদ্ধদেবের মুখে এমন অদ্ভুত বাণী শ্রবণ করে শিষ্যগণ অভিভূত হয়ে গেলেন। তাঁরা কিছুই প্রায় না বুঝতে পেরে কেমন ভয়বিহ্বল হয়ে পড়লেন, তাঁরা বুদ্ধদেবের কাছ থেকে আরেকটু সহজবোধ্য কথা শোনার আশা করেছিলেন। এই অজ্ঞান জগতের হৃৎকমলে যে আন্তরিক আস্পৃহা বিদ্যমান, বুদ্ধদেব তাকে মানতেন। তাই, সেই আস্পৃহাকে মেনে নিয়ে, তাঁর শিষ্যদের ঐকান্তিক ইচ্ছাপূরণের নিমিত্ত তিনি বললেন, “হে মোর একনিষ্ঠ ভক্তগণ! আনন্দ জানতে চায় কিভাবে সে তার মনের অবলোকনের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করবে। এ সেই অবলোকন, যা নিত্য, যা আপাত প্রপঞ্চের সমস্ত কিছুতে অচঞ্চল, যে তার তন্মাত্র মনের স্বরূপ। ওর প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে আমি ওকে সঙ্গে করে এক অতীন্দ্রিয় চূড়ান্ত দিব্য দর্শণে নিয়ে যাব। আর তা করব বলে, আমি এই মুহূর্তে আমার তথাগতের দর্শণ, তা সাময়িক পরিত্যাগ করব। তথাগত দর্শণ সেই অতীন্দ্রিয় দিব্য দর্শণ যা সম্যক বুদ্ধ-জগতে সর্বত্রগামী।
অতএব এস আনন্দ, আমার সঙ্গে এস, চল, আমরা সূর্য চন্দ্রের প্রাসাদে যাই, দেখ দেখি সেখানে কিছু দেখতে পাও কিনা যা আমাদের দিব্য তন্মাত্র মনের অধীন? চল যাই সুমেরু পর্বতের চারপাশের পর্বতের স্বর্ণশিখরে, ভাল করে দেখ আনন্দ, কি দেখতে পাচ্ছ? দেখতে পাচ্ছ কি সমস্ত রকমের ঔজ্জ্বল্য, সমস্ত প্রকার মহিমার বহিঃপ্রকাশ, তথাপি আমাদের তন্মাত্র মনের কিছুরই দর্শণ হয় না। আচ্ছা বেশ, আরেকটু কাছে যাই, চল মেঘের কাছে যাই, পাখি উড়ে বেড়াচ্ছে দেখতে পাচ্ছ আনন্দ, লক্ষ্য করছ ঝোড়ো হাওয়া বইছে, ধূলো উড়ছে, পর্বত, জঙ্গল, বৃক্ষরাজি, নদীসমূহ, পশুপাখী, গাছপালা, সবই দৃশ্যমান, অথচ কিছুই আমাদের তন্মাত্র মনের অংশ নয়।
“আনন্দ, এ সমস্ত বস্তু, কি দূর কি নিকট, তোমার নয়নের তন্মাত্রতায় অবলোকিত হচ্ছে, তাদের নানান রূপ, তথাপি তোমার তন্মাত্র মনের যে অবলোকন, সে অভেদ। এ থেকে মনে হয় না কি যে, দৃশ্য অবলোকনের এই যে অদ্ভুত তন্মাত্রতা, এই যে না স্থাবর না জঙ্গম অবস্থা, এ-ই আমাদের মনের স্বরূপ?”
এই কথা শুনে আনন্দ জানতে চাইলেন যদি তাই হয়, যদি দৃশ্য অবলোকনের ক্ষমতা, যদি দৃষ্টি অনুভব, তার স্বাভাবিক ক্ষমতাবলে দ্যাবাপৃথিবী পরিব্যাপ্ত করে, তবে এখন, এই এখন, যখন তিনি আর বুদ্ধদেব একই সভাগৃহে অবস্থিত, তখন তাঁদের দৃষ্টি কেমন ভাবে, দেওয়াল, আর ঘরেতেই আপাত সীমাবদ্ধ? দেওয়ালের ওপারে কি আছে তাতে দৃষ্টি আটকায় কি করে? “আনন্দ, এই যে প্রাচীর উঠেছৈ, আর চোখের দৃষ্টি আটকে ওপারে কিছু দেখা যায়না, বা ধর প্রাচীর যদি না থাকত, বা ভেঙে যেত তাহলে সব কিছু দেখতে পেতে, বা আলোকোজ্জ্বল তাই সব দেখা যাচ্ছে, বা অন্ধকার তাই কিছু দেখছি না, তাদের সঙ্গে দৃশ্য অবলোকনের সারবত্তার কোন সম্পর্ক নেই । এই যে নানারকম পরিবর্তনশীল অবস্থা, তা আমাদের “দর্শণ অবলোকনের” অংশও নয়। দর্শণ অবলোকন আমাদের তন্মাত্র মন, সে মহাশূন্যের মতন, সে না স্থাবর না জঙ্গম।
“আনন্দ, প্রাচীর আছে তাই বলে প্রাচীর প্রকৃত শূন্যতাকে আড়াল করে না, আবার প্রকৃত শূন্যতাও প্রাচীরের অবয়বকে নিশ্চিহ্ন করে না।“
তখন বুদ্ধদেব বললেন, “মনে কর আনন্দ, তুমি আর আমি বাগানে গিয়ে চারপাশ অবলোকন করতে থাকলাম, চন্দ্র-সূর্য দেখলাম, আরো নানান প্রকার বস্তু অবলোকন করলাম, কিন্তু এমন কোন “বস্তু” নেই যা কিনা দর্শণের অনুভূতি, যা আমাদের কেউ দেখাতে পারে। কিন্তু, এই যে নানান বিষয়, তাদের মধ্যে তুমি আমাকে এমন কিছু দেখাতে পারবে কি যা আমাদের দৃষ্টির অনুভূতির বাইরে?”
আনন্দ বললেন, “হে প্রভু! সত্য, আমি বুঝতে পেরেছি যে তাবৎ বস্তু, ক্ষুদ্র কি বৃহৎ, যেখানেই তাদের প্রকাশ হোক, তারা সবই দৃষ্টির অবলোকনের অধীন।” বুদ্ধদেব আনন্দের সঙ্গে একমত হয়ে বললেন, “তাই আনন্দ, তাই।” তখন সেখানে সমবেত অপেক্ষাকৃত নবীন শিষ্যগণ — বয়োবৃদ্ধ যাঁরা ধ্যান সমাপ্ত করেছেন, তাঁরা বাদে — বুদ্ধদেব ও আনন্দের এই কথোপকথন শ্রবণ করে, এর মর্মার্থ অনুধাবন না করতে পেরে হতবিহ্বল হয়ে, কিছুটা ভীত হয়ে, নিজেদের সম্বিৎ হারিয়ে ফেললেন।
তথাগত তাঁদের শান্ত করে বললেন, “হে মোর ভক্তগণ! পরম ধর্মগুরু যা শিক্ষা দিয়েছেন তা একান্তই তাঁর আন্তরিক বাণী, এতে অতিকথন বা অদ্ভুত কিছু নেই। এতে অহেতুক প্রহেলিকাও কিছু নেই। এ শিক্ষা নিয়ে বিচলিত হয়ো না, এতে অহেতুক দুঃখ কি আহ্লাদেরও কিছু নেই, বরং একে গভীরভাবে বিচার করে দেখো।”
দশম অধ্যায়
মঞ্জুশ্রী উঠে সমবেত শিষ্যমণ্ডলীর হয়ে জানতে চাইলেন, এই যে আমরা যা কিছু দেখি আমাদের দৃষ্টির চেতনার জন্যই তাদের অস্তিত্ব, নাকি তারা আমাদের দৃষ্টি চেতনার অংশ, এই দ্বিধাবোধ যদি বুদ্ধদেব বুঝিয়ে বলেন, এই বলে বললেন, “এমন করে বুঝিয়ে বলুন যাতে সব ভাইয়েরা প্রাঞ্জল করে বুঝতে পারেন, সহজ ভাবে কিন্তু বোঝানো চাই।”
বুদ্ধদেব উত্তর দিলেন, “মঞ্জুশ্রী ও অন্যান্য শিষ্যগণ: দৃষ্টির অনুভূতি যেখানে মহাসমুদ্র, দেখা যেখানে সেই সমুদ্রের বুকে ওঠা তরঙ্গমাত্র, সেখানে দেখা চেতনার অংশ নাকি নয়, এই নিয়ে দ্বিধাবোধের কিছু আছে কি?”
“তথাগতগণ মহাবিশ্বের দশদিকে অবস্থান করেন, মহাপ্রাজ্ঞ গণের সঙ্গে মিশে তাঁরা বাক্যে কি বাক্যরহিত অবস্থায় শিক্ষা প্রদান করেন; যেহেতু তাঁরা সতত পরমানন্দে নিবেশিত, তাঁরা সকল বস্তুর কার্যকারণ ও তার সম্বন্ধে ধারণাকে আকাশকুসুম জ্ঞান করেন, তাদের সৎ কি আপন অস্তিত্ব বলে কিছু থাকে না, তাদের সবটাই কারণজাত তাৎক্ষণিক এক কাল্পনিক অবস্থামাত্র।
“এই যে অভূতপূর্ব, আলোকিত দৃষ্টিচেতনা, বস্তু কি বস্তুর অবলোকন, এ সবই তন্মাত্র মনের অংশ।
“তাই, কেউ যখন বহি:প্রকাশকে দেখে, যা কিনা চেতনার সঙ্গে বস্তুর সংযোগে জাত কাল্পনিক কুসুমসম, তখন সে যেন খেয়াল রাখে যে এ সবই মায়া, এতে কোন রকম দ্বিধাবোধের অবকাশ নেই, দুতিন রকম মানে করার কিছু নেই।
তখন আনন্দ, বুদ্ধদেবের এই য়ে শিক্ষা — দৃষ্টির সৎ অবলোকনেই তাঁর আপন তন্মাত্র মন, আর নানারকম দৃশ্যের বহিঃপ্রকাশ খুব সূক্ষ্মভাবে দেখলে এর অংশ কেননা তাদের স্ব-প্রকৃতি বলে কিছু নেই, তারা মহাসমুদ্রে উথ্থিত তরঙ্গমাত্র, অজ্ঞানতাবশত তাদের উৎপত্তি ও নিবৃত্তি — এর প্রতি পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করে জানতে চাইলেন, এ সমস্ত বোধ কিভাবে কাজ করে, তিনি আপন হৃদয়ে যা বিশ্বাস করেন কিভাবে তাকে নিজের মনে অনুধাবন করবেন ।
এই কথা শুনে বুদ্ধদেব কেমন করে চোখ মায়ার ছলনায় ভোলে তার ব্যাখ্যা করলেন।
“আনন্দ, আমাদের চোখ মায়াবশত ভুলের ফাঁদে পড়ে। তন্মাত্র যে মন, সে কিন্তু পড়ে না । যে মানুষের চোখের রোগ, সে প্রদীপের শিখার চারপাশে আলোর ছটা দেখতে পায়, এ আলোর ছটা তার তন্মাত্র অবিচল মন কিন্তু তৈরী করে রাখে নি, এ বোধ তার চোখের অসুস্থতা-হেতু মস্তিষ্ক-গত মনের ভেদবুদ্ধিপ্রসূত । আবার দেখ, সুস্থ চোখ শূন্যে কাল্পনিক গোল গোল বলের মত চলমান ছবি দেখে। অতএব একটা ব্যাপার জেনো, চোখ যেহেতু স্বাভাবিকভাবেই মায়ার দর্শণে আবিষ্ট, তাই চোখ দিয়ে তুমি যা দেখ তা সবই মায়ার তরঙ্গমাত্র। অনাদি অনন্ত কাল ধরে চোখে দেখা ব্যাপারটা এমনই হয়ে আসছে। তোমার যে চোখের দৃষ্টি আদৌ আছে, এই-ই তোমার কর্ম, তোমার অন্যকালে অন্যত্র অজ্ঞান কার্যের উত্তরাধিকার তুমি বয়ে চলেছ।
“তবে আনন্দ এ নিয়ে বিচলিত হয়ো না। শুধু সময়ের অপেক্ষা, তুমি তোমার দৃষ্টি ত্যাগ করবে, তখন তো দৃষ্টি ত্যাগ করেই দিয়েছ।
“আনন্দ, এ চোখ নামক জ্ঞানেন্দ্রিয়ই কেবল নয়, আর পাঁচটা জ্ঞানেন্দ্রিয় — কান, নাক, জিহ্বা, শরীর, মস্তিষ্ক, এরা সবই প্রকৃতিগতভাবে মায়াবী, সব মিথ্যা, যতদিন বাঁচবে শ্বাস নেবে, ততদিন তোমাকে মায়ার ছলনায় ভুলিয়ে বেড়াবে।
“এস, তোমায় দেখাই তোমার ষড়েন্দ্রিয় কেমন করে তোমাকে মায়ার ছলনায় ভুলিয়ে রেখেছে, কেমন করে তোমার উজ্জ্বল, পূর্ণ, শুদ্ধ, নিগূঢ়, ঐশ্বরিক সৎ পরম শূন্য তন্মাত্র মনকে ভুলিয়ে দেয়।
“দিনের বেলায় যেইমাত্র চোখ খুলে খালি চোখে আকাশের দিকে তাকাবে, অমনি কাল্পনিক ছোট ছোট গোলা নয়ত পুষ্পের কুসুম যেন চলে ফিরে বেড়াচ্ছে দেখতে পাবে; আরো অদ্ভুত দৃশ্য যেমন সূর্যের তেজ থেকে উদ্গত কণা যেন ছুটে আসছে, ছোট ছোট আলোর ঝিকমিকি, সব যেন সূর্যের আলোরই অংশ; কিন্তু কোথায় এই কাল্পনিক কুসুমের উৎস? আনন্দ, সহজ করে বললে এ সমস্তই মায়া। কেন মায়া? কারণ এই কাল্পনিক পুষ্পনিচয় যদি দৃষ্টির অংশ হত, তাহলে তাদেরও দেখার, দেখতে পাবার ক্ষমতা থাকত, তোমার চোখের জ্যোতির মতন, তুমি তাদের মাধ্যমে নিজেকে দেখতে পেতে। বা, যদি ধর এরা শূন্যেরই অংশ হত, তারা শূন্যেই আসত যেত হারাত কোথাও, তখন আর বলতে পারতে না যে শূন্য বলে কিছু আছে। একটা ব্যাপার স্থির জেনো আনন্দ, শূন্য আছে। আর এই যে দেখা, সেই দৃষ্টি যেন তন্মাত্র মনের গভীরে স্বপ্নহীন বিভোর নিদ্রা থেকে জেগে ওঠে, আর দৃশ্য অবলোকন করা তারই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। আনন্দ, কল্পনার কুসুমেরা একেকটি অসুস্থ ধোঁয়াশার ঈঙ্গিতমাত্র, আর আমরা তাকেই “সতেজ দৃষ্টিশক্তি” বলি। আর এই দৃষ্টিই অনাদি অনন্তকাল ধরে সজাগ প্রাণীকে মিথ্যা মায়ায় ভুলিয়ে এসেছে।
“তোমার “মনে হওয়ার” যে অনুভূতি, এও তাই। শরীরী মায়ার মিথ্যা অনুভূতি।”
“তা কেমন করে হবে প্রভু?”
“আনন্দ, শরীর মিথ্যা মায়ার ফাঁদে ভুল করে, মহামানসের অন্তর্নিহিত চেতনায় কোন ভুল হয় না। অসুস্থ শরীরে মানুষ বেদনা অনুভব করে, তার অবিচল তন্মাত্র মনে কিন্তু বেদনার কোন অনুভূতি নেই, শারীরিক-মন, দেহগত-মস্তিষ্কগত-মন শরীরের অসুস্থতাহেতু এই ভেদভাব করেছে। আবার একই রকম ভাবে, সুস্থ শরীর যে স্পর্শ অনুভব করে, এও কাল্পনিক, শূন্য। তাই জানবে যে, শরীরের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় যেহেতু স্পর্শের একটা মিথ্যা অনুভূতি থাকে, শরীর দিয়ে যা যা অনুভব কর তার সবটাই মিথ্যা তরঙ্গ বই কিছু নয়। অনাদি অনন্তকাল ধরে শরীরের সঙ্গে এইটাই হয়ে আসছে, তোমার শরীর বলে যে কিছু আছে, তোমার কর্মের হেতু, তোমার অন্যত্র অজ্ঞানতার উত্তরাধিকার।
“তবে আনন্দ এ নিয়ে বিচলিত হয়ো না। শরীর ত্যাগ শুধু সময়ের অপেক্ষা, তখন তো শরীর ত্যাগ করেই ফেলবে।
“দুহাতের তালু যখন ঘষাঘষি কর, মসৃণতার বোধ জাগে, উষ্ণতার বোধ প্রতীত হয়, খসখস কি শীতলতা বোধ হয়, কোথায়ইবা এই নানান রকম অনুভূতিবোধের উৎপত্তি? আনন্দ, সহজ করে বললে এ সমস্তই অদ্ভুত মিথ্যা মায়ার অনুভূতিবোধ। কেন জান? কারণ স্পর্শের অনুভূতি যদি হাতের অংশ হত, তাহলে সদাসর্বদা স্পর্শের অনুভূতি পাওয়া যেত, স্পর্শের অনুভূতি পাবার জন্য তালু ঘর্ষণের জন্য অপেক্ষা করতে হত না। বা, এমন যদি হত যে স্পর্শের অনুভূতি শরীরের অংশ না হয়ে শরীরাতীত কিছু, শূন্যের অংশ হত, তাহলে তাকে সদাসর্বদা শরীরের সর্বত্র অনুভব করতে, শুধু তালু ঘষে নয়।
“নিশ্চিত জেনো, এ শূন্য, আর স্পর্শ করার পর, অনুভূতি তন্মাত্র মনের গভীরে স্বপ্নহীন নিদ্রা থেকে জেগে ওঠে, আর স্পর্শের অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ হয়। আনন্দ, স্পর্শের অনুভূতি একটা অসুস্থ ধোঁয়াশার চিহ্নমাত্র আমরা যাকে “সুস্থ শরীর” বলে থাকি, যা সচেতন প্রাণীদের অনাদি অনন্তকাল ধরে শারীরি অনুভূতির মিথ্যা মায়ার ছলনায় ভুলিয়ে এসেছে।
“তোমার শ্রবণ-অনুভূতিও তাই: কানের মিথ্যা অনুভূতি।”
“কেমন করে, প্রভু?”
“আনন্দ, কান মিথ্যা মায়ার ফাঁদে ভুল করে, মহামানসের অন্তর্নিহিত চেতনায় কোন ভুল হয় না। কানের অসুখে মানুষ মাথার মধ্যে গর্জন শুনতে পায়, তার অবিচল তন্মাত্র মন কিন্তু এ গর্জনের উৎস নয়। এ তার রুগ্ন কানের কারণে তার শারীরিক-মস্তিষ্ক-গত মনের ভেদবোধ। একই রকম ভাবে সুস্থ কান, শূন্যে শব্দ শোনে, যে শব্দ অস্তিত্বহীন। অতএব জেনো, কান যেহেতু তার স্বাভাবিক ক্ষমতাহেতু শব্দের মায়ায় মিথ্যা অবলোকনে আবিষ্ট, কান দিয়ে যা কিছু শুনতে পাও তার সবটাই মায়াতরঙ্গ। কানের সঙ্গে অনাদি অনন্তকাল ধরে এমনটাই হয়ে এসেছে, কান যে তোমার আছে, তা তোমার কর্মহেতু, অন্যকালে অন্যত্র তোমার অজ্ঞানতাহেতু কৃতকর্মের উত্তরাধিকার।
“কিন্তু আনন্দ, এ নিয়ে তুমি যেন বিচলিত হয়ো না, কান ত্যাগ করা শুধু সময়ের অপেক্ষা, আর তখন তো তুমি এ কান ত্যাগ করেই ফেলেছ।
“আমার ঘণ্টাধ্বনি যখন তুমি শুনতে পাও, তখন তথাকথিত শব্দতরঙ্গ তোমার কর্ণপটাহে আঘাত করে তাই তুমি ঘন্টার আওয়াজ শুনতে পাও, কিন্তু এই তথাকথিত শব্দের উৎস কি? আনন্দ,সহজ কথায় এ এক মিথ্যা অবাস্তবতা।
কেন?
কারণ শব্দের উৎস যদি কান হত, তাহলে স্বভাবত শব্দের উৎস ঘন্টা নয়, সেক্ষেত্রে কানে সদাসর্বদা ঘন্টাধ্বনি শুনতে পেতে, তার জন্য ঘন্টা বাজানোর জন্য অপেক্ষা করার প্রয়োজন হত না। বা যদি ধর শব্দ যদি ঘন্টারই অংশ হত, শব্দ যদি ঘন্টার ওপর নির্ভর করে থাকত কি ঘন্টাতেই শব্দের উৎস হত, ঘন্টা হতে শব্দতরঙ্গ প্রবাহিত হত, তাহলে কান ঘন্টার শব্দ বা ঘন্টায় কাঠি পড়া, এদের একের থেকে অন্যটাকে পৃথক করত কি? শব্দ যদি না কান না ঘন্টা কারো থেকেই না আসত, সে তবে আকাশে কল্পনার কুসুম হত, খামখেয়ালী শূন্যতায় তার অস্তিত্ব, এ হল সেই তরঙ্গ যাকে সচেতন প্রাণীগণ শব্দ নামে প্রকার বিভেদ করে। যাঁরা পরম জ্ঞানী তাঁরা আপাত অবয়ব আর দেওয়া নামকে সত্য বলে কখনো মনে করেন না। যেইমাত্র আপাতদৃশ্যমান অবয়ব আর নামকে সরিয়ে ফেলা যায়, যখন আর কোন বিভেদবোধ থাকে না, যেটুকু, যা পড়ে থাকে, সেইটাই বস্তুর সৎ, তন্মাত্রিক অবস্থা। অতএব সেই তন্মাত্রিক অবস্থার যেহেতু আপন গুণ বা বিধেয় বলে আর কিছুই নেই, থাকে না, থাকা সম্ভব নয়, থাকার কথা নয়, এই নির্যাসই তথতা, তার প্রকৃত রূপ। এই সর্বব্যাপী, অদ্ভুত, অভেদ, অভেদ্য, তথতাই একমাত্র সারসত্য, যদিচ তাকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করা হয় — পরমসৎ, সদসৎ, তন্মাত্র মন, তূরীয় বোধ, মহতী প্রজ্ঞা এই রকম বিবিধ প্রকার ধারণা। এই যে অরূপ, অশব্দ কি শব্দাতীত, সৎচিৎ এর যে ধর্ম, এই ধর্মকেই বুদ্ধগণ কালান্তরে প্রচার করে চলেছেন। যেইমাত্র পার্থিব উন্মাদ কলরোল ঝনঝনানি স্তব্ধ হবে, তখন শব্দের কল্পনাবোধটুকু আর থাকবে না, তবু, তখনো, শ্রবণচেতনা জেগে থাকবে এক পরম শূন্যতায়। একটা ব্যাপার স্থির জেনো আনন্দ, এ শূন্য, আর আমার ঘন্টা বাজানো মাত্রই তন্মাত্র মনের গভীরে স্বপ্নহীন সুপ্তি হতে চেতনা জেগে উঠল, আর তখনই শব্দের শ্রবণের প্রকাশ হল।
“শব্দ, যা কিনা তরঙ্গ, তুমি বলতেই পার এ তরঙ্গ সত্য, আর এও ঠিক, যেহেতু এ তরঙ্গ, এও এখনি নিস্তরঙ্গ হবে, আর তাই সারসত্যে এখন তরঙ্গ অস্তিত্ব বিহীন।
“আনন্দ, শব্দ শুনতে পাওয়া এক অসুস্থ ধোঁয়াশার চিহ্নমাত্র যাকে আমরা সুস্থ কান বলি, যার হেতু অনাদি অনন্তকাল হতে সচেতন প্রাণিকূল শব্দের মিথ্যা মায়ার ছলনায় ভুলে চলেছে।
“তোমার আঘ্রাণচেতনারও ওই একই অবস্থা, এও নাসিকার মিথ্যা বোধ।
“কি করে প্রভু?”
“আনন্দ, নাক ভুল করে, মনের অন্তর্নিহিত চেতনায় কোন ভুল বা মায়ার ছলনা হয় না। নাকের অসুস্থতায় মানুষ দুর্গন্ধ পায়, এ কিন্তু তার অবিচল তন্মাত্র মন সঞ্জাত নয়, এ বোধ তার অসুস্থ নাক হেতু মস্তিষ্কগত-মনের। একই রকম ভাবে সুস্থ নাক গন্ধ পায়, যে গন্ধ কাল্পনিক, যে গন্ধ শূন্যে অবস্থিত। অতএব জেনো নাক যেহেতু তার স্বভাব অনুযায়ী ঘ্রাণের মিথ্যাবোধে বিভূষিত, তোমার নাক দিয়ে যা যা আঘ্রাণ পাও, তার সবটাই মিথ্যা মায়া। নাকের সঙ্গে অনাদি অনন্তকাল ধরে এইটাই হয়ে আসছে। তোমার যে নাক আছে, এই গোটা ব্যাপারটাই তোমার কর্মের অংশ; অন্যত্র তোমার অজ্ঞানতাবশত কর্মের উত্তরাধিকার।
“তব আনন্দ এতে উতলা হয়ো না, আর কদিন পরে তোমার নাক বিসর্জন দেবে, তখন তো নাক বিসর্জন দিয়েই দিয়েছ।
“ফুল যখন ফোটে, এই প্রস্ফুটন তার ক্ষণমাত্র জীবনের মুহূর্তের বিস্ফোরণ। এই পুষ্পদল যখন তোমার কাছে কেউ রাখে, প্রস্ফুটিত পুষ্পের সেই সূক্ষ্ম কণাগুলি শূন্যপথে তোমার নাকে এসে আঘাত করে, তুমি সুগন্ধ আঘ্রাণ কর। তথাপি, এই সুগন্ধের উৎপত্তি কোথায় আনন্দ? আনন্দ, সহজ কথায়, এ এক মিথ্যা কাল্পনিক আঘ্রাণ। কেন? কারণ, এই গন্ধের উৎপত্তি যদি নাকেই হবে, তাহলে ফুলের গন্ধ পাবার জন্য নাককে ফুল ফোটার জন্য অপেক্ষা করতে হয় কেন? নাক তো সদাসর্বদা ফুলের গন্ধ পেত, গন্ধ এই ব্যাপারটির জন্য তাকে ফুল সাজানোর অপেক্ষায় থাকতে হত না। অতএব গন্ধের উৎস নিশ্চযই ফুলের মধ্যে, আবার তাই যদি হবে, তাহলে গন্ধের জন্য নাক থাকার প্রয়োজন কি? কেনই বা নাক কে নানান রকম গন্ধের প্রভেদ করতে হয়? বা চোখ কেন গন্ধ পায় না? কান কেন গন্ধ পায় না? আবার যদি ফুল আর গন্ধের সত্তা তাদের আপন হত, তবে চরাচর জুড়ে শুধুই গন্ধ বিরাজ করত। আবার যদি গন্ধের উৎস নাকে না হয়ে, ফুলে না হয়ে, তোমার নাক আর ফুলের মাঝখানের শূন্যস্থানে কোথাও হত আনন্দ, তোমাকে স্বীকার করতেই হত যে গন্ধ কোথাও থেকে আসছে যাচ্ছে, সে আসে যায়, শূন্যে কোথাও বা হারিয়ে যায়। তখন তো আর শূন্য স্থান বলে কিছু থাকত না। শূন্যস্থান যে আছে, এ নিয়ে তো সন্দেহ নেই, এ তুমি স্থির নিশ্চিত জান, আর ফুলের গন্ধ পাওয়া মাত্র, তন্মাত্র মনের গভীরে স্বপনহীন সুপ্তি হতে নিখিল চেতনা জেগে উঠলেন, আর নাকের নিজ নিজ অবস্থা অনুযায়ী ঘ্রাণের বোধ জাগ্রত হল।
“আনন্দ, গন্ধ পাওয়া, আমরা যাকে সুস্থ নাক নামে জানি, সে এক অসুস্থ ধোঁয়াশার চিহ্ন মাত্র, যার প্রভাবে চেতন প্রাণীগণ অনাদি অনন্ত কাল ধরে মিথ্যা মায়ার ছলনায ভুলে আসছেন, যা হওয়া উচিৎ তার উল্টো পথে সব কিছু চলতে থাকে।
“তোমার স্বাদেরও সেই এক অবস্থা, জিহ্বার মিথ্যা অবলোকন।
“কেমন করে, প্রভু?”
“আনন্দ, বলতে পার ব্যঞ্জনের স্বাদ ওই কাঠের পাত্রটির কাছে কেমন লাগে? আনন্দ, মহামানসের অন্তর্নিহিত চেতনা নয়, আমাদের জিভই কেবল মিথ্যা মায়ার ফাঁদে পড়ে। যে মানুষের জিভ রুগ্ন, তার কাছে সব কিছু বিস্বদ লাগে, খাবার তুলোর মতন বোধ হয়, এ স্বাদ কিন্তু তার অবিচলিত তন্মাত্র মনের কারণে নয়, এ বোধ তার অসুস্থ জিভের হেতু মস্তিষ্কগত-মনের ভেদবোধ। একই রকম ভাবে সুস্থ জিভ স্বাদ গন্ধ পায়, যে স্বাদ গন্ধ প্রকৃতপক্ষে কাল্পনিক, শূন্যে অবস্থিত। অতএব একটা ব্যাপার জেনো যে জিভের স্বাভাবিক ক্ষমতাবলে সে স্বাদের মায়ায় ভোলে, তাই জিভ দিয়ে যা কিছুর তুমি স্বাদ পাও সবটাই মায়া, মায়ার তরঙ্গ। অনাদি অনন্তকাল ধরে জিভের সঙ্গে এইটাই হয়ে আসছে; জিভ যে তোমার আছে, এটাই জেনো তোমার কর্মের অংশ, অন্যত্র অজ্ঞানবশতঃ কৃতকর্মের ফল।
“তবে আনন্দ, এ নিয়ে বিচলিত হয়োনা, এতো শুধু সময়ের অপেক্ষা, তোমার জিভ তুমি ত্যাগ করবে, আর তখন তো জিভ ত্যাগ করেই দিয়েছ।
“ব্যঞ্জনের রস যখন তোমার রন্ধ্রের সংস্পর্শে আসে, সে তোমার কি আমার, ঝাল ঝাল মশলার স্বাদ পাই, জিভের স্বাদ বয়ে নিয়ে যাওয়া নালিকাগুলো সে স্বাদ যখন বইতে থাকে, যখন স্বাদের বোধ জাগে, আমরা অভ্যাসবশতঃ বলি খেতে ভাল লাগছে, নয়ত বলি খেতে তত ভাল লাগছে না, কিন্তু এই স্বাদগন্ধের উৎপত্তি কোথায়? আনন্দ সহজ করে বললে, স্বাদের গোটা ব্যাপারটা একটা উদ্ভট কল্পনা; কিন্তু কেন বলতো? কারণ স্বাদের উৎস যদি জিভ হত, স্বভাবতই, স্বাদ জাগানোর জন্য তো ব্যঞ্জনের প্রয়োজন হত না, কিন্তু আমরা এও দেখি যে খাবার মুখে দেবার পরই স্বাদ পাই। বা ধর, স্বাদ যদি ব্যঞ্জনরসের অংশ হত, তাহলে কাঠের ওই পাত্র অপেক্ষা জিহ্বার স্বাদ গ্রহণের আর কিই বা পার্থক্য হত? আনন্দ, স্বাদ, শূন্যে একটি কল্পনা বই কিছু নয়, আর স্বাদ গ্রহণ করা মাত্র, নিখিল বোধি তাঁর তন্মাত্র মনের গভীরে স্বপ্নহীন নিদ্রা হতে জাগ্রত হলেন, অমনি জিহ্বার অবস্থানুযায়ী স্বাদ প্রকাশ পেল।
“আনন্দ, স্বাদ যে আছে, এ এক অসুস্থ ধোঁয়াশাকে নির্দেশ করে, যাকে আমরা “সুস্থ জিহ্বা” বলি, যে অনাদি অনন্তকাল ধরে চেতন প্রাণীকূলকে স্বাদের মিথ্যা মায়ায় ভুলিয়ে দুঃখ দিয়ে চলেছে।
“একই ব্যাপার তোমার চিন্তার অবলোকন নিয়েও, মস্তিষ্কের ভ্রান্ত অবলোকন”
“সে আবার কি, প্রভু?”
“আনন্দ, মহামানসের অন্তর্নিহিত বোধিতে কোন ভুল নেই, আমাদের মস্তিষ্ক মিথ্যা মায়ার ফাঁদে পড়ে। অসুস্থ মস্তিষ্কে মানুষ কল্পনা করে তাকে ভূতে পেয়েছে, এ কিন্তু তার অচঞ্চল, স্ফটিক-স্বচ্ছ তন্মাত্র মনের ধারণা নয়, এ তার অসুস্থ মস্তিষ্কের মস্তিষ্কগত-মনের বিভেদবোধ। একই ভাবে, সুস্থ মস্তিষ্কে মানুষ নানারকমের চিন্তাভাবনা করে, যার সবটাই শূন্যে কাল্পনিক। তাই একটা ব্যাপার জেনো আনন্দ, মস্তিষ্কের যেহেতু ভেদবুদ্ধিগত চিন্তার আর মিথ্যা অবলোকনের ক্ষমতা আছে, তোমার তাবৎ মস্তিষ্কগত ধারণা অলীক তরঙ্গ বই কিছু নয়। আবার এও দেখ আনন্দ, মহতী প্রজ্ঞার যে সজ্ঞাত আত্মবোধ, যার উৎস তূরীয় জ্ঞান, যে জ্ঞান সৎ চিৎ কে প্রকাশ করে, কাল হতে কালান্তরে যে ধারণাতীত বুদ্ধ-রূপের ক্রিয়া, যে পরম পরিপূর্ণতা সদাসর্বদাসর্বব্যাপী, অপিচ, যখন তোমার চেতনবোধ সেই আলোকের দর্শণলাভ করে, সেই আলোক যা অদ্যাবধি মেঘাবৃত চন্দ্রের ন্যায় তোমার মস্তিষ্ক আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, সে কিন্তু আনন্দ নামের বুদ্বুদে আবৃত মস্তিষ্কসঞ্জাত নিছক ব্যক্তিগত বিভেদবুদ্ধির চিন্তা নয়। মিথ্যা মায়ার ব্যস্ত চিন্তা মানুষকে অজ্ঞতা আর কর্মের বাঁধনে গ্রথিত করে, মস্তিষ্কের অবলোকন, অনাদি অনন্তকাল ধরে এইটাই হয়ে আসছে। তোমার যে মস্তিষ্ক আছে ও জন্ম হতে এততকাল ধরে তার বৃদ্ধি ও বিকাশ হয়েছে, এ জানবে তোমার কর্মহেতু, অজ্ঞানবশতঃ অন্যকালে অন্যত্র কৃতকর্মের ফল।
“তবে আনন্দ, এতে বিচলিত হয়ো না। কারণ, শুধু সময়ের অপেক্ষা, তার পর একে তুমি ত্যাগ করবে, তখন তো সে ত্যক্ত।
“আবির্ভাব অন্তর্ধানের এই যে পরস্পরবিরোধী, দ্বৈত, অতএব অলীক ধারণা, এই ধারণার বশবর্তী হয়েই মস্তিষ্ক চিন্তাভাবনার জন্ম দেয়। সুস্থ চোখ যেমন আকাশে কুসুম দেখে, যে কুসুমের অস্তিত্ব না তার চোখে, না সে আকাশে অবস্থিত, সম্পূর্ণ কাল্পনিক, মস্তিষ্কও সেই রকম নানান চিন্তার উদ্গাতা। সেই সব চিন্তা আসে যায়, কিন্তু না তারা মস্তিষ্কের অংশ, না অন্য কিছুর, পুরোটাই কাল্পনিক। আমাদের মনের অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে সপ্তপথে এই শতসহস্র নিয়ত প্রবহমান চিন্তার উৎস কোথায় বলতে পার আনন্দ? এই যে মহামানসজাত তন্মাত্র মনের অযুতসহস্র বুদ্বুদ, এর প্রত্যেকটি একেকটি মায়া বই কিছু নয়। কেন? যদি এই বয়ে চলা চিন্তাতরঙ্গের উৎস মস্তিষ্কে হত, চিন্তা যদি মস্তিষ্কের অঙ্গ হত, তাহলে কেনই বা সে ক্ষণমাত্র জাত হয়েই মিলিয়ে যাবে, এমন শতসহস্র চিন্তার আগমন নির্গমনের জায়গা করে দিয়ে সরে যাবে? যেমন এই ধর ভাবছ কোথাও বেড়াতে যাবে, তার ক্ষণমাত্র পরেই ভাবছ রাত্রে কি খাবে । এ নিশ্চয়ই স্বপ্ন, আনন্দ, এ সমস্ত স্বপ্নই। বা ধর, চিন্তার উৎস যদি মস্তিষ্কের বাইরে অন্য কোথাও হত, তখন, মস্তিষ্ক বলে যদি কিছু না থাকত, তাহলে চিন্তাও থাকত না। তার মানে চিন্তা ব্যাপারটা পুরোটাই অলীক।
“তবে জেনো, এ সব শূন্যে বিরাজমান অশরীরী অস্তিত্ব, মস্তিষ্কে তাদের উদয় অস্ত অনুধাবন করে, তন্মাত্র মনের গভীরে স্বপ্নহীন নিদ্রা হতে নিখিল অবলোকন জেগে উঠলেন, আর তন্মাত্র মনের অরূপ আনন্দে চিন্তা-চেতনার আবির্ভাব হল।
“আনন্দ, চিন্তার চিন্তায় সেই অসুস্থ ধোঁয়াশার অবস্থামাত্র, যাকে আমরা সুস্থ মন বলি, অনাদি অনন্তকাল ধরে যে চেতন প্রাণিকূলকে মিথ্যা মায়ায় ভুলিয়ে রেখেছে, জন্ম-মৃত্যু-অস্তিত্বের ক্রমাগত বয়ে চলা দাসত্বের ফাঁদে।
“যাঁরা প্রজ্ঞা অর্জন করেছেন, যাঁরা অনস্তিত্বকে (বা অস্তিত্ব) আর অবলোকন করেন না, অস্তিত্বকে যাঁরা বুদ্বুদতুল্য জ্ঞান করেন, যেন নিদ্রা হতে জাগরিত হলেন, তাঁদের পূর্বজন্ম যেন কেবলই স্বপ্ন।
ষড়েন্দ্রিয় যে কেবলই মায়া, এ শিক্ষা আনন্দের মজ্জায় মজ্জায় গ্রথিত হয়ে যাবার কথা। তবু তাঁর চিন্তাশীল মনে ক্ষিতি-অপ-তেজ-মরুৎ-ব্যোম-এর যে আপাত বস্তুশীলতা আর তাদের পরিবর্তনশীলতা, এই নিয়ে একটা দ্বিধাবোধ ছিল। বুদ্ধদেবের শিক্ষানুযায়ী এ সমস্ত অনন্ত তন্মাত্র মনের প্রকাশ বই আর কিছু নয়। শ্রদ্ধার সঙ্গে তাই তিনি আবার বুদ্ধদেবকে জিজ্ঞাসা করলেন। শান্ত মনে, চুপ করে মন দিয়ে বসে রইলেন, মহৎ জনের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবেন, এই আশায় উন্মুখ হয়ে রইলেন।
বুদ্ধদেব বললেন, “আনন্দ, যেমনটি তুমি বললে, এই পৃথিবীতে প্রকারভেদ, আর পরিবর্তনশীলতা, যার সঙ্গে আমাদের বিষয়ী মন তার ষড়েন্দ্রিয় নিয়ে সংশ্লিষ্ট, তার প্রকাশ চারটি বৃহৎ বিষয়বস্তকে নিয়ে (ক্ষিতি, অপ, মরুৎ, তেজ); আরো তিনটি বিষয়বস্তু — ব্যোম, ধারণা, চেতনা — সব মিলিয়ে সাত বস্তুর সমভিব্যাহার। ক্ষিতি, ধরিত্রী, দিয়ে শুরু করি।
“ক্ষিতি (ধরিত্রী) কিরূপে বুদ্বুদ? আনন্দ, প্রশ্ন রাখা যেতে পারে যে বুদ্বুদের অভ্যন্তর শূন্য নাকি শূন্য নয়? ধরিত্রী যেহেতু ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ধূলিকণার সমন্বয়ে গঠিত, যাকে অণু পরমাণু অবধি অনন্ত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র স্তরে ভাবা যেতে পারে, তাই প্রতিটি অণুতে যেন বিশ্বেরই প্রকাশ। জ্ঞানীজন তাই উপলব্ধি করেন যে চোখের পাতায় পাতায় মহাবিশ্বের উপস্থিতি, গঙ্গার অযুত বালুকারাশি যেমন অনন্ত, তাঁরাও তেমনি অনন্ত। আনন্দ, বলতো এই অপ্রাকৃৎ বিশাল শূন্যতায় কি হয়ে চলেছে?
“ভাল করে তাকিয়ে দেখ আনন্দ! তাবৎ বস্তুকে ভেদ করে দৃষ্টিনিক্ষেপ করে দেখ আনন্দ, দেখবে সর্বত্র সুপ্রাচীন বুদ্ধগণের অপার করুণাহৃদয়ের প্রকাশ। একেই বলা হয় যথাভূতম, তাবৎ বস্তুনিচয়কে তাদের মতন করে দেখা।
“মাটির চরিত্রকেই ভেবে দেখ। একদিক থেকে দেখলে মনে হবে সে ভূপৃষ্ঠকে ঢেকে রেখেছে। আবার খুব সূক্ষ্মভাবে বিচার করে দেখলে মাটি শূন্যে অবস্থিত ধূলির অণুপরমাণু , কেবল তাই নয়, চোখ যা দেখতে পায় সব কিছুই এইরকম আদিম প্রাথমিক তত্ত্বে নামিয়ে আনা যায়, যা চোখে দেখি সবটাই কেবল মাটি, মাটি বই কিছু নয়। তোমার তো জানা কথাই আনন্দ, এই যে পৃথিবী, অনুপরমাণুর ধূলিধূসরিত এই শূন্যময়তা, তাকে যদি সত্যি সত্যি মহাশূন্যের পরম শূন্যতায় নামিয়ে এনে দেখা যেত, তবে সেই অবাংমনসগোচর পরমতা থেকে দৃষ্টির ব্যাপারটিও তখন প্রকাশ পেত।
“আনন্দ, ভূমির তন্মাত্রিক চরিত্র আসলে মহাশূন্যের শূন্যতা বই আর কিছু নয়, সত্যিকারের মহাশূন্যতা; আবার মহাশূন্যের তন্মাত্রিক চরিত্র প্রকৃত ভূমি, এই তার সৎ চরিত্র।
“তথাগতের অনজাত গর্ভে সর্ব বস্তুর অজাত অবস্থাই শেষ ও পরম অনুভূতি, মহাশূন্য আর দর্শণ চিরনবীন, সদসৎ, সে মহাবিশ্বের সর্বত্রগামী, সদাসর্বদা কর্মহেতু সদা প্রকাশমান, সজাত প্রাণীর অজ্ঞানতার কৃতকর্মহেতু তাকে দৃষ্টি কি স্বপ্ন বলে ভ্রম করে। মানুষ, মনসিজ প্রাগৈতিহাসিক দৈত্যপ্রায় প্রেতচ্ছায়া, জানেনা তার আপন অস্তিত্বের তত্ত্ব, অতএব প্রাকৃতিক কার্যকারণে হতবিহ্বল হয়ে পড়ে, ভাবে পৃথিবীর বুঝি আপন কোন অন্তর্লীন চরিত্র আছে, তাকে প্রকৃতি বলে, ধরিত্রী-মাতা বলে জ্ঞান করে, তাদের নিজস্ব দেহাতীত মানসরূপ ধারণ করায়, মনে করে এসবের স্রস্টা বুঝি আপন রূপকল্পে একে গড়েছেন, তারপর তার অস্তিত্বকে নিজেদের মত করে “সময়ের” মাপে বিচার করে, অণু, পল, ক্ষণ, আপনাপন অনুভূতি, সবই মানুষের নিজের চেতনাগত মনের,বাক্যের ধারণার এক থেকে আরেকটিকে পৃথক করে দেখার প্রয়াস, এসবের সত্যিকারের কোন অর্থ নেই।
“আনন্দ, এই অণু-পরমাণু-ধূলিকণা কোথা থেকে আসে, কোথায়ই বা যায়, কোথায়ই বা তার অবস্থান?” কেউ যেন তোমাকে ডেকে বলছে, “দৃষ্টি নিবি? নে না! কত দৃষ্টি তোর চাই, যত দৃষ্টি চাস, নিয়ে যা!” অথচ তুমি কারো কাছে কিছু চাও নি। যেস্থানে পৃথিবীর জন্ম, সেস্থান সর্বত্র বিরাজমান, পৃথিবী তাই সদাসর্বত্র বিরাজমান। অস্যার্থ, পৃথিবীর আপন অস্তিত্ব প্রমাণ করে অণুপরমাণু আর তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের সূত্রেই আমাদের কাছে পৃথিবীর প্রকাশ। কে বা কারা, তারা কিভাবে একসঙ্গে মিলে পৃথিবীর জন্ম দিয়েছিল? তন্মাত্র মনই ধরিত্রী নামক ব্যাপারের উৎস।”
আনন্দ জানতে চাইলেন, “প্রভু, জল উপাদান সম্বন্ধে বলুন ।”
পরম জন বললেন, “জল কেন স্বপ্ন, আনন্দ? প্রশ্ন করা যেতে পারে যে স্বপ্ন সত্যি না মিথ্যা?”
আনন্দ, জলের উপাদানের বিষয়টা বিচার করে দেখি। জল স্বভাবত অনিত্য, নদীর স্রোত বা সমুদ্রের ঢেউ, যাই হোক। ভোরবেলা সূর্য ওঠে, শিশির উত্তপ্ত হয়, পাত্রে বিন্দু বিন্দু জল জমে। কি মনে হয় আনন্দ? এই বারিবিন্দুর উৎপত্তি কি শিশিরে, না কি শূন্যে, না কি সূর্যে তার উৎপত্তি? সূর্য থেকে তার যদি উৎপত্তি হত, তাহলে যেইমাত্র সূর্যোদয় হত, সর্বত্র জল দেখা যেত, কিন্তু এও আমরা দেখি যে জল জমতে গেলে শিশিরকে থাকতেই হবে। যদি ধর শিশির থেকেই জল আসত তাহলে আবার জল হতে গেলে সূর্য উঠে গরম হওয়া অবধি অপেক্ষাই বা করতে হবে কেন? আবার যদি কেবলই শিশির থাকত আর জল না হত, তাহলে বলা যেত জলের উৎপত্তি সূর্যে নয়। আবার জল যদি সূর্য আর শিশিরের মাঝে যে অপার শূন্যতা, সেখান থেকে আসত, তাহলে, শূন্যতা তো অপার, জলও যদি অপার হত, তাহলে কি পৃথিবীতে, কি আকাশে, সচেতন প্রাণীকূলের জলে ডুবে যাওয়ার একটা ব্যাপার থাকত। আবার তুমি যদি বল যে জল সূর্য, শিশির, আর শূন্যতা, তিন অবস্থা থেকেই উদ্ভুত, তবে তুমি হয়ত বলবে যে তার তিন তিনটে উৎস। জল তাহলে কোথা থেকে আসে? কোনখানেই নেই সে, এটাও তো হতে পারে না। আবার, মনে কর যেখানে যেখানে শিশির পড়বে, সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সেখানে জল হয়ে যাবে, সারা পৃথিবীতে সর্বত্র শিশির পড়ে, সর্বত্র জলে জল, এর কি বা তাৎপর্য?
“আনন্দ! কেন তোমরা অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন হয়ে আছ না বুঝে যে জলের অন্তর্নিহিত, যথাযথ স্বরূপ শূন্যতায়, আর মহাশূন্যের প্রকৃতি জল-মাত্রতা!
“উজ্জ্বল শূন্যতার স্বরূপে তন্মাত্র মন, জল আর শূন্যতা সেখানে পরম চিরনবীন রূপে সদা বিরাজমান, মহাবিশ্বের সর্বত্র তারা বিরাজিত, মুক্ত, চেতন প্রাণীর আপন কর্মবলে তারা সদা বিকশিত।
“তথাপি, ইহজগতের মানব, তারা এ বিষয়ে অজ্ঞ, জলকে তারা কার্য কারণ, উপাদান নিদান বলে ধরে নেয়, বিহ্বল হয়ে পড়ে। এই সব মিথ্যা ধারণা আর কুসংস্কার, সব মনের ভিতর, এদের কারো কোন সত্যিকারের ভিত্তি নেই।
“কোথা থেকে জল উৎপন্ন হয়, কোথায় সে থাকে, কোথায়ই বা সে যায়? জলের উৎপত্তি সর্বত্র, যেখানে যা দেখি সবেতে তার উৎপত্তি। অস্যার্থ, সূর্যোদয়ে শিশির গলে মিশে যে অবস্থা তাতে সে আছে, তবু কেবল এই অবস্থাই জলের একমাত্র উৎস নয়, জল নামের এই প্রপঞ্চের উৎস তন্মাত্র মন। “
আনন্দ বললেন, “প্রভু, অগ্নি নামক উপাদানটি সম্বন্ধে আমাদের বলুন।”
পরমকারুণিক বুদ্ধদেব বললেন, “অগ্নি কেন ধারণা, আনন্দ? চিন্তার উদয় হয়েছে না কি সে অন্তর্হিত, সে প্রশ্ন করা যাবে কি?
“আনন্দ, অগ্নি নামক উপাদানটির কথা বিচার করে দেখ। আগুনের নিজস্ব কোন প্রকৃতি নেই, সে অন্যান্য অবস্থার উপর নির্ভরশীল। শ্রাবস্তীনগরে দ্বিপ্রহরে মানুষ যখন রান্না প্রস্তুত করে, সেই সময় যদি তাদের দেখ, দেখবে ঘরে ঘরে মানুষ আতস কাঁচ দিয়ে সূর্যের আলো সোমরাজ গাছের শুকনো কাঠের ওপর ধরে তাতে আগুন জ্বালায়। আগুন কিন্তু মধ্যাহ্ন, আতস কাঁচ, আর শুকনো কাঠে উথ্থিত হয়নি। কেন? কারণ শুকনো সোমরাজ কাঠের ওপর দিবা দ্বিপ্রহরে কেউ যখন আতস কাঁচ ধরে আগুন জ্বালায়, সে আগুন আতস কাঁচ সঞ্জাত, না কি তার উৎস সোমরাজ কাঠে, না কি সূর্যে, আনন্দ? আগুন যদি কেবল সূর্য হতেই সঞ্জাত হত, তবে ঐ সোমরাজ বনে আগুন লাগে না কেন? যদি আতস কাঁচ থেকে আগুনের উৎস হত, তাহলে আতস কাঁচ নিজে পোড়ে না কেন, আনন্দ? এমনিতে, যতক্ষণ না তোমার হাত আতস কাঁচ সোমরাজ গাছের শুকনো ডালপালার ওপরে দিবা দ্বিপ্রহরে প্রখর রৌদ্রে না ধরবে, তদবধি তো আগুনের আবির্ভাব হবে না। ভাল করে ভেবে দেখ আনন্দ! কিছু কিছু অবস্থাবিশেষে আগুনের আবির্ভাব হয়। তুমি তো তোমার হাতে আতস কাঁচ ধরে আছ, সূর্যের আলো আসছে সূর্যের থেকে, সোমরাজ গাছের ডালপালা গজিয়েছে মাটি থেকে, আগুন তাহলে কোথা থেকে এল, সে থাকেই বা কি করে, যায়ই বা কোথায়? বলতে তো পারবে না সে কোথাও থেকে আসেনি।
“কেন তুমি জান না আনন্দ, যে, আগুনের একান্ত সত্তা শূন্যতা, আবার শূন্যের একান্ত সত্তাই অগ্নি। তথাগতের গর্ভে, আগুন ও শূন্যতা পরম সৎ অবস্থায় সহাবস্থান করে, মহাবিশ্বের সর্বত্র তাদের ব্যাপ্তি, সচেতন প্রাণীকূল আপনাপন কর্মবলে তাদের উপলব্ধি করে। অতএব একথা জেনো আনন্দ, এই পৃথিবীতে যখন যেখানেই মানুষ শুকনো কাঠের ওপর প্রখর সূর্যালোকে আতস কাঁচ ধরবে, তখনই সেখানে আগুনের উৎপত্তি হবে। আগুন সর্বত্র; তথাপি এই সব অবস্থা সাপেক্ষে তার প্রকাশ হয় নি। সে আপন নিয়মে নিজে নিজেও জ্বলে না। যদি তাই হত, তাহলে সদাসর্বদা সর্বত্র আগুন জ্বলত। আর যদি ধর সর্বত্র সদাসর্বদা আগুন জ্বলতে থাকত, আগুন ছাড়া কিছু না থাকত, তাহলেই বা কি বোঝা যেত? মনে হত না যে এই নিখিলব্যাপী আগুনই নিখিল মানস? বা, ধর যদি সর্বত্র শুধু জল থাকত, আর কিছু না থাকত, তাতেও কি মনে হত না যে জগদ্ব্যাপী জলই নিখিল মানস? কিন্তু কি দেখি? এখানে জল, ওখানে আগুন, কেননা তারা তাদের অবস্থা সাপেক্ষে উদ্ভুত, একে অপরকে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে পরিবর্তিত করে চলেছে। যেমন জল দেখ টগবগ করে ফুটছে, তাকে আগুনের ওপর ঢাললে, আগুন নিভে গেল, আবার সেই জল বরফে পরিবর্তিত হল। এ ক্রিয়া চলতেই থাকে। মানুষ এ পৃথিবীতে এ বিষয়ে অজ্ঞানতিমিরে পড়ে আছে, আগুনকে কার্য কারণের প্রকাশ বলে ধরে নেয়, বা হয়ত ভাবে আগুন নিজে নিজেই জ্বলে ওঠে, ভাবে আর হতবাক হয়ে যায়। অথচ, ভেবে দেখলে দেখ, এই যে মানুষের ভ্রান্ত ধারণা, এই যে সব কুসংস্কারই ধর, এসবই তাদের চেতনায় যে সমস্ত এক থেকে অন্যতে পৃথক বোধ, বিভেদবোধ, তারই প্রকাশ, শব্দে বাক্যে তাদের সে প্রকাশ করে, এর কোন বাস্তব অস্তিত্ব নেই, এ বাস্তবিক অর্থহীন।
“আনন্দ, আগুনও যা, আবর্জনাও তাই। আবর্জনার সৎ, পরম, মূল চরিত্রগত দিক থেকে বিবেচনা করলে তাকে দেখে ঘৃণা করারও কিছু নেই, আবার ঘৃণা না করারও কিছু নেই, কিন্তু সেই পরম সত্তাকে কেই বা আর ভেবে দেখে?”
আনন্দ বললেন, “প্রভু, বায়ু-উপাদান নিয়ে বলুন। “
পরমশ্রদ্ধেয়জন উত্তর দিলেন, “বায়ু কেন প্রতিফলন আনন্দ? এই প্রশ্ন করা যেতে পারে কি যে প্রতিফলন নিত্য না কি অনিত্য?”
“বায়ুর চরিত্র বিবেচনা করে দেখি। সে যখন সচল কি স্থির, তাকে দেখাও যায় না, তার কোন নিত্য অবস্থাও নেই। একটা উদাহরণ দিই, আমি যদি তোমার মুখের সামনে হাত নাড়াই, তোমার মুখে মৃদু হাওয়া বয়ে যায়, কেমন? তোমার কি মনে হয় আনন্দ, এই যেই হাত নাড়ালাম অমনি হাওয়া বইতে শুরু করল তোমার মুখের ওপর, এ কি আয়নায় প্রতিফলনের মতন আমার হাতে তার উৎস, না কি তোমার মুখ আর আমার হাতের মধ্যবর্তী হাওয়ায় তার উৎপত্তি? যদি আমার হাত থেকে তার উৎপত্তি হত, তবে এই যে আমার দুই হাত এখন আমার দুই জানুর ওপর রেখেছি, কই হাওয়া বইছে না তো! যদি মাঝের শূন্য স্থানে তার উৎপত্তি হত, তবে তুমি যে গলবস্ত্র পরে আছ, তা স্থির থাকে কি বলে? শুধু তাই নয়, যদি ধর আমার হাত আর তোমার মুখের মাঝের শূন্যতা থেকে সে আসত, তবে এই নিত্য শূন্যতায় সারাক্ষণ বায়ু প্রবাহিত হত। তা যখন হচ্ছে না, তার মানে কি শূন্যতা নেই? তা তো নয়। এই যে হাওয়া বয়, আসে যায়, কে যায়? কি প্রবাহিত হয়? কি এর রূপ? এই যে যাওয়া আসা, শূন্যতার অপ্রকাশ প্রকাশ, মৃত্যু, পুনর্জন্ম, শূন্যতা আর বলা যাবে না। আবার যদি শূন্যতা বলতে, তবে এই মহাশূন্যতা থেকে বায়ু আসে কিভাবে? এই যে মুখে মৃদু সমীরণের স্পর্শ, তা যদি মুখ থেকে উদিত হত, তবে সদাসর্বদা মুখে হাওয়ার স্পর্শ লেগে থাকত। বায়ুপ্রবাহের উৎস কোথায়, সে আসে কোথা থেকে? বায়ুপ্রবাহ শূন্যে যেন গভীর নিদ্রায় মগ্ন, আমার হাতের দোলায় তাকে জাগালাম, তবু হাওয়ার জন্ম আমার হাতের মুদ্রার দোলানিতে নেই, কারণ আমার হাত যখন স্থির, তখন সেই মৃদুমন্দ বায়ু তো আর সেখানে ফিরে আসে না? আমার হাত শূন্যে, আবার সমীরণ সর্বত্র। বায়ু যদি সর্বত্র হতে আসত,কোথায়ই বা তার উৎস খুঁজে পেতাম?
“আনন্দ! কেন তোমরা এই অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন, যে, তূষিতের জগতে, যে কিনা তাবৎ অস্তিত্ব কি অনস্তিত্বের ধারণার অতীত, বায়ুর তন্মাত্র চরিত্রে সে সতত শূন্য, আর শূন্যতার সতত চরিত্রে সে বায়ু।
“শূন্যতাকে নিয়েও তাই, সে পঞ্চম মহা উপাদান। আনন্দ, শূন্য, তার তন্মাত্রিক অবস্থায়, শূন্যের কোন রূপ নেই, সে অরূপ, কারণ এ এক স্ফটিকতূল্য স্বচ্ছ শূন্যতা যাকে আমরা আমাদের মনে এমন করে মেনে নিয়েছি যে সে যেন আমাদের চেন জানা কিছু কিছুর মাঝে রয়েছে, যেমন দুটি তারার মাঝে, এক কাল্পনিক বিভাজন। রঙের মাধ্যমে আমাদের ইন্দ্রিয়ে শূন্যের প্রকাশ, যেমন আকাশে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ধূলিকণায় সূর্যালোক বিকিরিত হয়ে নীলাকাশ দেখায় চোখে। তবু আর সকলের মতই শূন্যতাও একটা ধারণা, কেননা শূন্যতা বলেও, যেন গ্রহ হতে গ্রহান্তরে, কি প্রাকারের মধ্যে শূন্যস্থানে কিছু আছে, আসলে কিছুই নেই।
“ধর একটা কূয়ো খুঁড়ছ। খুঁড়তে খুঁড়তে মাটির ওপরে ধুলোর স্তুপ করলে, আর মাটির নীচে শূন্যতা। যখন একটা কূয়ো খনন করা হল, তখন একটিমাত্র কূয়োর সূত্র ধরে শূন্যতার বহিঃপ্রকাশ দেখলে। আবার যখন মহাবিশ্বের দশদিকে সর্বত্র শূন্য, সর্বত্রই সেই শূন্যতার প্রকাশ। শূন্যতা যখন সর্বত্রগামী, তখন তাকে কোথায়ই বা আলাদা করে খুঁজে পাবে? কিন্তু পৃথিবীতে সকলে অজ্ঞানতিমিরে আচ্ছন্ন হয়ে, অবাক হয়ে পড়ে আছে, কেননা তারা সতত শূন্যতাকে কার্যকারণহেতু প্রকাশিত বলে ভেবে এসেছে, যেমন মাটি খুঁড়ে গর্ত করলে সেখানে যা থাকে না, তাই শূন্য। অথচ, শূন্যের প্রকৃত রূপ তার সদাসর্বদা উপস্থিতিতেই, তার ‘অ’-শূন্যতায়, একে উপলন্ধি করাই প্রকৃত বোধ, আলোকপ্রাপ্তি। স্তুপ করে রাখা ধুলোর রাশি শূন্যতাকে আড়াল করতে পারে না, আবার শূন্যতার শূন্যময়তাও ধুলোর রাশিকেও নিশ্চিহ্ন করে দেয় না। খেয়াল করে দেখ শূন্য কোন অদেখা জায়গা থেকে আসে না, আবার কে বা কিই বা দেখা, কিই বা অদেখা? সে কি বহিরঙ্গে কিছু দেখা বা না দেখার বোধ থেকে উদিত, কেননা আমরা তো জানি যে দৃষ্টির অবলোকন মায়া, মিথ্যা! না কি সে না আসে, না যায়?
“আনন্দ, তুমি জান না যে, তথাগতের গর্ভে শূন্যতা আর বোধির তন্মাত্রতা সদাসর্বদা পবিত্র হয়ে প্রস্ফুটিত, তারা মরজগতের সর্বত্রগামী, সর্বব্যাপী, অযাচিতভাবে তাঁরা সজীব প্রাণীকূলের আপনাপন কর্মানুযায়ী প্রকাশিত।
“ভূমি, জল, অগ্নি, আর বায়ুর সঙ্গে শূন্যকে পঞ্চ মহা উপাদান বলে ধরা হয়, যাদের তন্মাত্র প্রকৃতি পরিপূর্ণ, এরা একভাবে তথাগতের গর্ভে বিচরণ করেন, এরা একমেবাদ্বিতীয়ম, এদের মৃত্যু কি পুনর্জন্ম বলে কিছু নেই।
“আনন্দ, আমি তথাগতের গর্ভের ও তথতার উল্লেখ করলাম যাতে তুমি এইসব অতি সাধারণ মামুলি শিক্ষা আর ধ্যানধারণার অতীত যে উজ্জ্বল দুর্জ্ঞেয় জ্ঞান রয়েছে তাতে মন দিতে পার। আমি তথাগতের বিষয়ে বলি বটে, বলে থাকি যে তাঁরা আসা-যাওয়া, শিক্ষা-না-শিক্ষার ঊর্দ্ধে বিচরণ করেন, তথাপি আমার বাক্য কেবল সৎচিতের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে মাত্র, আমার বাক্যকেই সত্য বলে ধরে নেওয়ার কিছু নেই। প্রকৃত সত্যের স্বরূপ কোনদিনই উদ্ঘাটিত হবার নয়, কেননা অস্তিত্ব ব্যাপারটিই যে একটা মিথ্যা কল্পনা।
“পরম সত্যের কথা বুদ্ধগণ প্রচার করেন বটে, কারণ, তাকে ব্যাখ্যা করতে “অস্তিত্ব” নামে ভাষার অলংকারের ধার না ধারলেও উপায় নেই, তবে জেনো যে ব্যাপারটার পুরোটাই আলঙ্কারিক।
“বলতে গেলে, পরম সত্যের ধারণাটি এতটাই বিশাল, অগম্য, যে বলা যায়, প্রকৃত সৎ বলে কিছুই নেই।
“প্রকৃত সৎ বলেও কিছু নেই, অসৎ বলেও কিছু নেই, থাকার মধ্যে কেবলই তন্মাত্রতা। আর সেই তন্মাত্রতার যখন একটা ধারণা হয়, তাকে বলি তন্মাত্র মন।
“আনন্দ, “অবলোকন” বা অনুভব হচ্ছে ষষ্ঠ মহা উপাদান। আমরা সচরাচর একে দেখার অনুভূতি, শোনার অনুভূতি, ঘ্রাণের অনুভূতি, স্বাদের অনুভূতি, স্পর্শের অনুভূতি, চিন্তার অনুভব — এইরকম নানারকমের অনুভূতির, অনুভবের কথা বলি। আসলে চরিত্রগত ভাবে এ সবই একমেবাদ্বিতীয়ম — — এক অবলোকন মাত্র। আপন চরিত্রে সে অভিন্ন।
“আমাদের ষড়েন্দ্রিয় অবলোকনকে ছ ভাগে বিভক্ত করে রাখে, মনে কর একটা রেশমি রুমাল, তাতে ছ ছটা গিঁট, তারপর যেই গিঁটগুলো খুলে ফেলবে দেখবে তখন দেখবে একটাই রুমাল, এও তাই, একটাই অবলোকন, যত ইচ্ছে গিঁট বাঁধোনা কেন।
“যেখানেই চোখ, সেখানেই আলো-আঁধারি-দৃশ্যের ধারণা, সেখানেই দর্শণের অবলোকন অবিশম্ভাবী। চকমকি পাথর ঘষলে যেমন আগুনের ফুলকি বেরোয়।
“নাক যেখানে, নাকের মধ্যে দিয়ে যাওয়া আসার বোধ, গন্ধ, সেখানে ঘ্রাণের অবলোকন হবেই।
“যেখানেই জিহ্বা, পরিবর্তন-অপরিবর্তনের ধারণা, রসগন্ধের সমব্যাহার, সেখানেই স্বাদের অবলোকন।
“যেখানে শরীর, স্পর্শের, দূরে সরে যাওয়ার চেতনা, সেখানেই স্পর্শের অবলোকন।
“যেখানে মস্তিষ্ক, সেখানে অবয়ব-অন্তর্ধান, চিন্তা চেতনার, সেখানে চিন্তার অবলোকন।
“অন্যান্য মহা উপাদানের মত, অবলোকনেরও কোন কার্য কারণে উৎপত্তি নেই, তথাপি সে তাদের প্রতি সংবেদনশীল, তার আপন কোন সত্তাও নেই, সে অতি সীমিত, যেমন ধর চিন্তার অবলোকন, অতি সীমিত, সে ক্ষণস্থায়ী।
“কিন্তু অবলোকনের যে তন্মাত্রতা, সেখানে সে কিন্তু পূর্ণ, সেখানে সে ভূমি, জল, বায়ু, অগ্নি, স্থানের সঙ্গে মিলে তথাগতের গর্ভে একসঙ্গে এক পরম তন্মাত্রতায় এক হয়ে গিয়েছে। সেখানে তার মৃত্যুও নেই, পুনর্জন্মও নেই।
“অবলোকনের সৎ চরিত্রে সে সত্যিকারের শূন্যতা। স্থানের তন্মাত্র চরিত্রেই তার অবলোকনের তন্মাত্রতা।
“অবলোকন কোথা থেকেই বা আসে, কোথায়ই বা সে যায়? যেখানেই দেখ, সর্বত্রই অবলোকন।
“চৈতন্য হল সপ্তম মহা উপাদান। আনন্দ, অনাথপিণ্ডক এই জেতবনে আমাদের যে সমস্ত ঝরণা আর জলাশয় গড়ে দিয়েছেন, সেগুলোর দিকে একবার দেখি। তাদের কাকচক্ষু জলে যে প্রশান্তি, মহাবিশ্বের দশদিকে প্রপঞ্চময় জগতব্যাপী এক চৈতন্য এই জলাশয়ের প্রশান্তিতে যেন মগ্ন হয়ে আছে, আর যেই আমাদের চোখের সঙ্গে এই জলাশয়ের, এই ঝরণার সংস্পর্শ হয়, সাতোরি জেগে ওঠে চৈতন্যরূপে জলাশয়ের আর ঝরণার অবয়বে, আমাদের মনে।
“এর পরেও কেন যে প্রশ্ন কর অস্তিত্ব কোথায় অবস্থিত? কোথায় তাকে খুঁজে পাব? চৈতন্য তো সবকিছুকেই মেনে নিয়েছে, চৈতন্য সর্বত্রগামী, সে সর্বব্যাপী, যখন না থাকে দৃষ্টি, না থাকে চিন্তা, তখন চৈতন্য কোথায় থাকে?
“আনন্দ, খুব স্বাভাবিক ভাবেই, খেয়াল করনি, যে তোমার তথাগতের গর্ভে চৈতন্যের তন্মাত্র চরিত্র নিহিত, না সে ঝর্ণা না সে জলাশয়ের দৃশ্য অবলোকন করে, আবার না সে না-চেতন। সে কেবল অ-বস্তুর ধর্ম সম্বন্ধেই সচেতন। আনন্দ, তুমি কি বলতে চাও যে পাথর আর জলাশয় এই দুটি একে অপরের থেকে পৃথক? তার চেয়ে বরং এ কথা যদি বলতে যে প্রত্যেকটিতেই বুদ্ধের প্রকাশ, আমাদের কেবল একটিমাত্র বুদ্ধেই কাজ, সে এক রকম হত। কারণ প্রতিটি বস্তুই অ-বস্তু, অতএব সব বস্তুই বুদ্ধ। এই যে বোধ, একেই “রত্ন সূত্র” বলা হয়। এ ব্যতীত আর সব, আর সব কিছুই যেন কেবল তরঙ্গের মতন চঞ্চল, আর বেলুনের মতন ফাঁপা। এই যে বোধি, এই তোমাদের পরম সৎ তন্মাত্র চৈতন্য, এ যেন শূন্যের তন্মাত্র চরিত্রের মতন। “
এই কথা শুনে আনন্দ ও সভাস্থিত আর সকলে ভগবান তথাগতের কাছ থেকে এই অপার্থিব গভীর শিক্ষা গ্রহণ করে, সকল প্রকার চিন্তা ও আকাঙ্খা হতে মোক্ষলাভ করলেন, কায়মনে সম্যক মুক্তিপ্রাপ্ত হলেন। তাঁরা প্রত্যেকে অনুধাবন করলেন, মহাবিশ্বের দশদিকে মন যেমন সতত সঞ্চরণশীল, তেমনি তাঁদের দৃশ্য অবলোকনের ক্ষমতাও মহাবিশ্বের দশদিকে গমন করতে পারগ। এ ধারণা তাঁদের কাছে হস্তে ধৃত তৃণবৎ সরল বোধ হল। তাঁরা দেখলেন যে প্রপঞ্চময় জগতব্যাপার তাঁদের অপূর্ব, পূর্ণ মানসজাত আলোক বই আর কিছু নয়। তাঁরা উপলব্ধি করলেন এই যে শরীর তাঁরা তাঁদের পূর্বপুরুষদের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয়েছেন, তা যেন মহাবিশ্বের দশদিকে সতত সঞ্চরমান ধূলিকণাবৎ। কেই বা এই ধূলির খবর রাখে? এক অনন্ত মহাসমুদ্রে ভাসমান ফেনার ন্যায় তাঁদের কায়া, কিছুই জানা যায় না কোথা থেকে এ ফেনা ভেসে এসেছে, কোথায়ই বা সে ভেসে যাবে। শুধু এইটুকু তাঁরা সম্যকরূপে উপলব্ধি করলেন যে দিনের শেষে তাঁরা এক অদ্ভুত মানসের বোধপ্রাপ্ত হয়েছেন, যে মানস অবিচল, যে মানস অবিনশ্বর।
তাই সভাস্থিত সকলে করজোড়ে ভগবান বুদ্ধদেবকে শ্রদ্ধাবনত হয়ে প্রণিপাত করলেন। তারপর সবাই সমবেত স্বরে ভগবান তথাগতের স্তবগান করলেন। বুদ্ধদেব এই কথা বলে শেষ করলেন,
“আনন্দ, আমাদের শরীরের কথা ভেবে দেখলে তোমার হয়ত অবাক লাগবে যে যদিও কার্য-কারণ একত্র হয়ে আছে, তথাপি কারণ কি না-কারণ এসবের কোনটাই যেন কিছু নয়।
“ইহকালে এই যে তোমার শরীর, আনন্দ, তা না কেবল তোমার পিতার ঔরস-প্রাপ্ত, না কেবল তোমার মাতার গর্ভ-সঞ্জাত, না কেবল পুষ্টিবলে তুমি তাকে প্রাপ্ত হয়েছ; আবার এমনও নয় যে এদের কারো কাছে তুমি তা পাও নি, তাহলে তো তোমার অস্তিত্বই থাকে না, আবার এও নয় যে তিনটির একত্রীকরণে তাকে তুমি প্রাপ্ত হয়েছ। পরম পবিত্র শূন্যতায় “যে” এতকাল অপেক্ষা করেছিল, “সে” কোনকালে বীজ, গর্ভ, আর পুষ্টির আহ্বানে সাড়া দিয়ে জাগরিত হল, “তার” কাছে প্রাপ্ত তোমার শরীর; “সে” যদি সাড়া না দিত, সে যদি বাহির না হত, তবে সে রয়ে যেত উজ্জ্বল পরম তন্মাত্র মনে। তোমার শরীর শুধু এইটুকুই প্রমাণ করে যে বীজ গর্ভে প্রবেশ করে পুষ্টিপ্রাপ্ত হলে তবেই শরীরের প্রকাশ হয়।
কেন বললাম এ কথা? পিতার বীজ যদি মাতার গর্ভে প্রবেশপূর্বক পুষ্টিপ্রাপ্ত না হত, তাহলে তো কোন কিছুর প্রকাশ হত না, সব কিছু উজ্জ্বল মানসেই নিহিত রয়ে যেত। তুমি হয়ত বলবে শুধু পিতার বীর্যহেতু তোমার শরীর? তাহলে পুরুষের শরীর থেকে শিশুর উদয় হয় না কেন? বলবে হয়ত শুধু মাতৃগর্ভ-সঞ্জাত শরীর? তাহলে সর্বত্র, সর্বকালে কেবল মাতৃগর্ভ হতে সন্তানের উদয় হত, বীর্য সন্নিধানের অপেক্ষা করতে হত না। তুমি হয়ত বলবে, পুষ্টি হেতু শরীরের উদয়? তাহলে কি সমুদ্রে কি প্রস্তরে পুষ্টি দিয়ে দিলেই মানবশরীরের জন্ম হত। হয়না তো । এদের কারো কাছেই শরীর তাহলে ঋণী নয় বলছ? আবার তাই বা কি করে হবে? বীজ, গর্ভ আর পুষ্টি তিন না থাকলে তোমার শরীরের যে অস্তিত্বই থাকে না। তার অর্থ কি এই শরীরের হেতু বীজ, গর্ভ, আর পুষ্টি — এই ত্রয়ীর সমষ্টিতে? এই যে তোমার শরীর, তার উৎপত্তি জেনো সাত মহা উপাদান থেকে। জন্ম আর কার্য একে অপরের সঙ্গে মিলেছে, পরিবর্তিত হয়েছে, তথাপি একত্র হয়নি, কারণ এরা যাবতীয় একত্রীকরণের উর্দ্ধে বিচরণ করে, যে যার তাদের আপন তন্মাত্র একতায়। এই যে জগদ্ব্যাপী অলৌকিক উপাদানসমূহ যত্র তত্র ছড়িয়ে আছে, তোমার শরীর তাদের পরিবাহী মাত্র, শরীর তাদের উৎপত্তি ও বিকাশকে গ্রহণ করে বটে, তথাপি সেই সব উপাদান নিজেরা অবিচল, তারা অক্ষয়, অজর, তাদের না জন্ম, না মৃত্যু, শরীর যখন চিতায় পোড়ে, তখনও তাঁরা অবিনশ্বর।
“শরীরের অস্তিত্ব শুধু এইটুকুই প্রমাণ করে যে নারী-পুরুষের মিলন, ইহজগতে শরীরের অবয়বের বহিঃপ্রকাশ হতে সাহায্য করে মাত্র। পুনর্জন্ম।
“তবে রহস্য কি জান? শরীর মানস-জাত, শরীর শরীরাতীত। তাই, তোমার শরীর, সে এক বাচ্যালংকার, তার না আছে অস্তিত্ব, না আছে অনস্তিত্ব, না আছে তার কোন কারণ, না আছে তার না-কারণ, কেননা মহা আলোকের তন্মাত্র মহামানস, যে কিনা সমস্ত প্রকার বিভেদবোধের উর্দ্ধে, সেখানে এসব কিছুই নেই। তোমার দেহের অবয়ব যখন দেখি, আমি দেখি শূন্যে যেন পুষ্প প্রস্ফুটিত, বাস্তবতা হতে সে বিযুক্ত। শরীরকে “যে” বা “যা” শরীরত্ব প্রদান করে, সেই উপাদান কোথা থেকে আসে, কোথায়ই বা সে যায়? আনন্দ, তারা সর্বত্রব্যাপী, তারা সব জায়গা থেকে আসে, এ এক অপার রহস্য-সাগর।
“আনন্দ, তোমার শরীর যেন চিন্তা, নিত্য তন্মাত্র মানসে অবস্থান করেও সে ক্ষণে ক্ষণে অনিত্য। চিন্তার আর মহামানসের তন্মাত্রতা একই, স্বাভাবিকভাবেই, কিন্তু অবয়ব ক্ষণিকের মায়ামাত্র, মহামানসের তন্মাত্র সর্বজ্ঞান যাকে আমরা তথাগতের গর্ভ বলে জানি, এ সেই অবয়বকে অগ্রাহ্য করে, না আছে তার অস্তিত্ব, না তার অনস্তিত্ব। কে কাকে দেখে? — অহংকারী এক শিশু যেন আয়নায় মুখ দেখে, আনন্দ?
সেই সমবেত সাধুমণ্ডলীতে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, এই বাণী শ্রবণ করে তাঁদের প্রত্যেকের মনে হল যেন কোন এক ঐশ্বরিক দানবীর মহারাজার কাছ থেকে তাঁরা এক ভারি সুরম্য প্রাসাদ উপহার পেলেন, কিন্ত হায়! সেই প্রাসাদের মালিকানা পেতে গেলে তাঁদের এক আলোকিত চেতনার তোরণ পেরিয়ে, সম্যক বোধির উজ্জ্বল কক্ষে প্রবেশ করতে হবে। না প্রবেশ করতে পারলে সে দান তাঁরা গ্রহণ করতে পারবেন না, ও সেখানে প্রবেশ করা অতি দুরূহ; তখন তাঁরা মহাপ্রভুর চরণতলে প্রণিপাত করে তাঁদের মুখপাত্র আনন্দকে দিয়ে বুদ্ধদেবের কাছে আরো কিছু শিক্ষা প্রদানের নিমিত্ত অনুনয় করলেন। বুদ্ধদেব যেন তাঁদের এমন শিক্ষা প্রদান করেন, যা তাঁরা তাঁদের ব্যবহারিক প্রাত্যহিক জীবনে চর্চা করতে পারবেন, ও চর্চা করতে করতে, অভ্যাস করতে করতে, তাঁরাও যেন কালক্রমে বুদ্ধদেবের যে প্রজ্ঞা ও অন্তর্দৃষ্টি, তা অর্জন করতে সক্ষম হন।
আনন্দ এই বলে শেষ করলেন, “ভগবান, আপনার কাছে প্রার্থনা করি, আমাদের পথ দেখান। পথ দেখান যে আমরা কি করে, কি উপায়ে, জগৎব্যাপারের এই যে জটিল কুটিল চক্রব্যূহ, তাকে ভেদ করতে সক্ষম হব; আমরা যারা অর্হৎ হবার অনুশীলনে রত, আমাদের মন যাতে ঠিক পথে চলে, একমনে একাগ্র থাকে, কিভাবে তা অর্জন করব।
একাদশ অধ্যায়
পরম জন তখন অপার করুণায়, পরম স্নেহে, আনন্দের মাথায় হাত রেখে বললেন, “আনন্দ, তোমার শরীরে ভূমির কঠিন উপাদান রয়েছে; জলের তরল উপাদান রয়েছে; রয়েছে আগুনের তেজোময়তা; রয়েছে শ্বাস প্রশ্বাসের মধ্য দিয়ে বায়বীয় উপাদানের গতিময়তা। আমাদের শরীর এই চার মহা উপাদানের দাস: আবার এই চার মহা উপাদান তোমার অপার, অলৌকিক, গূঢ়, মহা-আলোকিত মানস-কে দেখা, শোনা, আস্বাদন, আঘ্রাণ, স্পর্শ প্রভৃতি বোধ আর অনুভূতিতে বিভক্ত করে রেখেছে। তার ওপর ধারণা আর চিন্তার ভেদবুদ্ধি তোমার মহা-আলোকিত মানসকে দুষ্ট জগতের পঞ্চ-কলুষে নিমজ্জিত করে রেখেছে। জগতের আদিতেও যা ছিল, শেষের সেদিনও তাই হবে।
“কি এই পাঁচটি কলুষতা? পাঁচটি অপবিত্রতা? কি বা তাদের প্রকৃতি? মনে কর কোথাও বেশ টলটলে পরিষ্কার ঝরণার জল রয়েছে আর তারপর সেই জলে ছাই, ধুলোময়লা, বালি মিশিয়ে দেওয়া হল। সেই জল তখন অপরিষ্কার হবে, কলুষিত হবে। পাঁচ কলুষতা আর মনের ব্যাপারটাও অনেকটা সেই রকম।
“আনন্দ, যখন ঐ বিশাল মহাশূন্যের পানে দেখ, ঐ যে চরাচর ব্যাপী অসীম শূন্যতা, তার যে প্রকৃতি, আর দর্শণ অবলোকনের যে প্রকৃতি, তাদের মধ্যে কোন বিরোধ নেই, এমনকি তাদের আপনতা, তাদের নিজস্বতার মধ্যে কোন সীমারেখাও নেই । মহাকাশ যদি কেবলই শূন্য হত, তাতে যদি সূর্য বা গ্রহ তারা না থাকত, সে মহাশূন্যের সারগর্ভতা বলে কিছু থাকত না। কোন বস্তুর না থাকার অর্থ মহাশূন্যের কোন ধারণাও না থাকা। আবার দৃষ্টি, শূন্যে তাকিয়ে আছ, অথচ কিছু দেখার নেই, এই কথারও কোন মানে হয় না। যেহেতু এখানে দুটি অবাধ মিথ্যা ধারণা প্রসূত ব্যাপার ঘটছে — সূর্য-গ্রহেরা মহাশূন্যে বিচরণ করছেন, আবর্তন করছেন, দৃষ্টির বোধটিও একটি অলীক বোধ, এই ভাবে বিচার করে দেখলে চরাচর জুড়ে কেবলই অনন্ত অলীক আপাত দৃশ্যের সমভিব্যাহার।
“যেহেতু তোমরা উপলব্ধি কর না, যে, এ সবই মনের মায়া, সবটাই ব্যক্তিগত অনুভূতি, তোমরা ব্যক্তিত্ববোধের কলুষতার কবলে পড়, এই যে সবটাই নিজের মত করে দেখা, এই হচ্ছে প্রথম কলুষতার বুনিয়াদ।
“এই হচ্ছে প্রথম কলুষতা, প্রথম মালিন্য, ভেদবোধের কলুষতা।
“এরপর, প্রপঞ্চময় জগতের সমস্ত বিষয়কে একে অপরের থেকে পৃথক জ্ঞান করতে করতে এক সময় তোমাদের শরীর আর মনের প্রক্রিয়াগত ভাবে একে অপরের অলীক অবলোকনের সঙ্গে এমনভাবে মিলেমিশে যায় যে তোমরা খুব সূক্ষ্ম ব্যাপারগুলো খেয়াল কর, অবয়বের একে অপরের থেকে পার্থক্য সম্বন্ধ নানাপ্রকার ভ্রান্ত ধারণা থাকে, এইভাবে ক্রমশ ভুলে যাও যে অবয়বে অবয়বের গভীরে কেউ কারো থেকে পৃথক নয়। আলোর বস্তু আর আঁধারের বস্তু, সত্যিই কি এরা একে অপরের থেকে আলাদা?
“এ হল দ্বিতীয় কলুষতা, অবয়বের কলুষতা।
“তারপর, চেতনার প্রক্রিয়া হেতু অবয়বের নানা রকমের ধারণা জন্মেছে, এই অবস্থায় এই নানাপ্রকার অবয়বের এক থেকে অপরকে পৃথক করতে করতে এই নানান রকমের অবয়বের মধ্যে কাউকে একান্তভাবে চাও, কাউকে তীব্র ঘৃণা কর।
“তৃতীয় কলুষতা, কামনা-বাসনার কলুষতা।
“আবার, অবয়বের ভেদবোধ থেকে কামনা-বাসনা জন্মেছে, দেখ কেমন করে একটি থেকে অপরটির ধারণা জন্মে, বস্তুকে মানুষ আঁকড়ে ধরতে চায়, আঁকড়ে ধরতে চেয়ে বোঝে না তাদের স্বরূপ, যে, এ সমস্তই মায়া। দিবারাত্র তোমাদের মন পরিবর্তিত হয়, আর যেইমাত্র মনের, চিন্তার পরিবর্তন হয়, তাকে তোমরা কিছু একটা সৃষ্টি কর, করে, সৃষ্টির মাধ্যমে স্থির ধরে রাখতে চাও। যেইমাত্র তোমাদের কাজ, তোমাদের প্রারব্ধ কর্মের হেতু আকার ধারণ করে, তারা অন্যান্য সচেতন প্রাণকেও পরিবর্তিত করে দেয়। মিথ্যা মায়ার কল্পনাজালে একে অপরকে আবদ্ধ করে রাখে,চেতন প্রাণীকূল তাদের কাঙ্খিত বস্তুকে আঁকড়ে ধরতে চায়। কামনা-বাসনা জানবে বন্ধুর বেশে শত্রু।
“এই আঁকড়ে ধরে থাকা চতুর্থ কলুষতা, আঁকড়ে ধরার কলুষতা।
“সব শেষে, তন্মাত্র মনের পরম চেতনায় তোমাদের দেখা, শোনা, ছোঁওয়া, চিন্তা, ঘ্রাণে, আস্বাদনে কোন তারতম্য নেই, এরা সকলে একে অপরের সঙ্গে পরিপূরক, অথচ যেই তারা একের বিরুদ্ধে অপরে মুখোমুখি হয়, তখনই তারা একের বিরুদ্ধাচরণ করতে থাকে। এই ভাবে অন্তরে বাহিরে দ্বিধাদ্বন্দের সৃষ্টি হয়, কালক্রমে, জরা বার্ধক্য আসে। এ হল পঞ্চম কলুষতা, দৌর্বল্যের, জরার, অসুখের, মৃত্যুর কলুষতা।
“কেন আনন্দ? কেন তোমরা বস্তুর কামনায় তাকে আঁকড়ে ধরতে চেয়ে, সেই অনিত্য অবয়ব, যার নাকি থাকার কথাই ছিল না, তার জন্য জরায়, দৌর্বল্যে নিমজ্জিত হও?
“আনন্দ! তুমি যখন ধ্যান কর, তোমার ধ্যানমগ্ন অবস্থায় শান্ত সমাহিত মনে যখনই এলোমেলো চিন্তার উদয় হবে, তখনি তাকে এই পাঁচ কলুষতার পেষন যন্ত্রে একে একে তাদের উৎসে ফিরিয়ে নিয়ে যেও, তাদেরকে সম্যকরূপে পরীক্ষা করে দেখো যে তারা কিভাবে তোমার মনের প্রশান্তিকে নষ্ট করার উপক্রম করছে; দেখবে কোথাও কিছু একটাকে আঁকড়ে ধরা, কাউকে চাওয়ার কারণে, কোন অবয়বের কারণে, ভেদবুদ্ধিজনিত অজ্ঞানতার কারণে এ সব ঘটে। একই রকম ভাবে কাজের চাপে পড়ে মনে যখন কুচিন্তার,আবেগের, আসক্তির, কামনা-বাসনার উদয় হয়, সেই আবেগকেও পঞ্চ-কলুষতার নিষ্পেষণী-যন্ত্রে পাঠিয়ে নিজেকে জিজ্ঞাসা কর, “আনন্দ, যে মূর্ততা কেবল একটি ভেদবুদ্ধিগত কল্পনা বই আর কিছু নয়, তাকে চেয়ে কেন তুমি নিজেকে দুঃখভোগ আর দৌর্বল্যের পঙ্কে নিমজ্জিত হতে দিচ্ছ?”
“আনন্দ! তুমি যদি তোমার ইন্দ্রিয়ানুভূতি আর সচেতন বোধকে তথাগতের চিরন্তন পরমানন্দ বোধির সুরধুনীর সঙ্গে মিলিয়ে দিতে চাও, তাহলে সর্বাগ্রে তোমাকে মৃত্যু ও পুনর্জন্মের যে শিকড় পঞ্চ-কলুষতা, অর্থাৎ — ভেদবুদ্ধির অজ্ঞানতা, অবয়ব, কামনা-বাসনা, আঁকড়ে ধরা না ত্যাগ করতে শেখা আর দৌর্বল্যের — কলুষতা, প্রোথিত করেছে, তাকে উপড়ে ফেলতে হবে। তারপর না-মৃত্যু, না-পুনর্জন্মের যে তন্মাত্র মন, তাতে পূর্ণ ধ্যান ও মনোনিবেশের নিয়ত অভ্যাস শুরু করতে হবে।
“হ্যাঁ আনন্দ, প্রশান্ত মনে, একটি গাছের তলায় বা অন্যত্র উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করে উপবেশন কর। তারপর চোখ বন্ধ কর। ধীরে ধীরে, শান্ত মনে শ্বাস প্রশ্বাস নিতে থাক, শরীরটাকে শিথিল করে দাও, বিশ্রাম নাও, মনে মনে মহা আলোকের কথা স্মরণে আন, আর চিন্তা করতে থাক: ‘এ মন অমৃত, এ মন অ-পুনর্জাত, এ মন পরম পবিত্র তন্মাত্র মন, এই উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কই পরম সত্য, এ ব্যতীত আর সবকিছু শুধু স্বপ্ন, শুধু মায়া।’
“তারপর যখন বোধ হবে যে কোন কিছু, বা কেউ, না জন্মায়, না মরে, তখন না অস্তিত্ব, না অনস্তিত্বের বোধ থাকবে, তখন শান্ত হবে মন । সেই শান্ত মনের পথ বেয়ে তুমি তোমার ঐ মৃত্যু আর পুনর্জন্মের মিথ্যা ধারণাপূর্ণ মায়া মনকে পালটে দেবে পরম সৎ, স্বচ্ছ পরমবোধি মনে; আর এই করতে করতে তোমার উজ্জ্বল, আদি, অবচেতন তন্মাত্র মনের নাগাল পাবে।
এভাবেই শুরু কর।
“তুমি যদি মনকে স্বচ্ছ, তুমি যদি মনকে তার আদি অকৃত্রিম তন্মাত্রতায় নিয়ে যেতে চাও, সেই প্রয়াস এমনভাবে চালিয়ে যাও যেন একটা পাত্র-পূর্ণ ঘোলা জলকে পরিষ্কার করার চেষ্টা করছ। জলের পাত্রটিকে খানিকক্ষণ এক জায়গায় রেখে দিতে হবে, জলের মধ্যে মিশে থাকা বালি-ময়লা নীচে থিতিয়ে গেলে তবে না সে জল পরিষ্কার হবে; মনের অবস্থাও তদ্রূপ; যত রকমের কুচিন্তা, কলুষতা, যা মনকে বিব্রত করে, তাদের থিতিয়ে যেতে দাও। তারপর স্বচ্ছ জল ছেঁকে বার কর; যখন অজ্ঞানতা, অবয়ব, বাসনা, আঁকড়ানো, দৌর্বল্য মন থেকে মুছে যাবে। মন যখন স্বচ্ছ, মন যখন সেই একমেবাদ্বিতীয়ম একমাত্রায় নিবেশিত হবে, সে তখন আর কোন বস্তুকে আলাদা করে দেখবে না, তাদের এমন করে দেখতে পাবে তারা যেন সব এক হয়ে গেছে, সেখানে কুচিন্তার, দুরাবেগের প্রবেশ করার কোন স্থান নেই, নির্বাণের অনির্বচনীয়, অপার্থিব পবিত্রতায় সব মিলে মিশে এক হয়ে আছে।
“আনন্দ! তাই বলে ক্ষণমাত্রের জন্যও ভেব না যে ক্ষণে ক্ষণে উথ্থিত চিন্তাতরঙ্গকে রুখেছ মানে মনও স্তব্ধ হয়েছে।
“ঠিক যেমন হঠাৎ করে ঘন্টা বাজালে মুহুর্তমাত্র শব্দ হয়, তারপর তার শব্দ ক্রমে ক্রমে মিলিয়ে যায়, আর তারপর আবার নৈঃশব্দ, তার মানে কি তোমার শ্রবণশক্তিও মিলিয়ে গেল?
“আনন্দ, এ কথা বলা অর্থহীন যে তোমার মন, তাবৎ জগতের আবির্ভাব অন্তর্ধান, মৃত্যু-পুনর্জন্ম, এইরকম সব নানান রকমের অবস্থা থেকে এতটাই পৃথক যে, চিন্তার যে অবলোকন, তার নিজের কোন তন্মাত্র অবস্থাই নেই। ওরকম হয় না।
“সকল সচেতন প্রাণী, অনাদি অনন্তকাল থেকে সুন্দর দৃশ্য,মধুর সঙ্গীত, সুখের অনুভূতি, আশ্চর্য আস্বাদ, সুগন্ধ,এসবের জন্য আকুল; মনে একের পর এক চিন্তা, চিন্তা থেকে ক্রমাগত কাজ, সদাসর্বদা ভাবে মনকে কাজে লাগাতে হবে, বোঝে না যে মন “কাজে লাগানোর” উর্দ্ধে, মানুষ কখনো উপলব্ধি করে না যে মনের চরিত্র পরম পবিত্র, মন তন্মাত্র, মন অপার্থিব; মানুষ ভাবে না বলে সে চিরন্তন পথে না চলে, সে পঞ্চশর, পঞ্চ-কলুষতার ফাঁদে পড়ে ক্ষণমাত্র, অনিত্যতা, মৃত্যু-পুনর্জন্মের পাকে পড়ে। যার ফলে জন্ম-জন্মান্তর ধরে কেবল কলুষতা, অনিত্য জীবনের সংগ্রাম, আর দুঃখভোগ।
“আনন্দ, জেতবনের মাটিতে পড়ে থাকা শত শত মৃত পাখির শবের মতন এই জীবন। এ প্রশ্নটা করা যাবে কি যাবে না, যে অবয়বে কি সুখ?
“আনন্দ, জন্ম-মৃত্যুর দাসত্ব শৃঙ্খল আর অনিত্য জীবনের ভীতি থেকে যদি মুক্তির পথ তুমি জানতে, যদি জানতে যে অক্ষয় অমরত্বে, যা কিনা অতীন্দ্রিয়, যার সঙ্গে সময় কি ত্বরিত জীবনের কোন সম্পর্ক নেই কেননা সে সুগত (সে-যে-সতত-সদাসর্বদা-সু), তাতে যদি যথাযথ মনোনিবেশ করতে পারতে, তাহলে সেই চীর-ঔজ্জ্বল্য তোমাকে আলোকমণ্ডিত করে রাখত, আর সেই অমল আলোয় ক্ষুদ্র, তুচ্ছ, ব্যক্তিকেন্দ্রিক ভেদবুদ্ধিগত ঘটনার অবলোকন, মিথ্যা কল্পনা আমি না-আমি, সব অপসৃয়মান, কেননা চিন্তন মস্তিষ্ক-মনের তাবৎ ধারণা মিথ্যা, সাময়িক, তোমার ভেদবোধগত মরজাগতিক চেতনা শুধু সাময়িক চলমান চিন্তা, আর কিছু নয়। তুমি যদি মৃত্যু-পুনর্জন্ম আর অনিত্যতার ভীতি — এই দুটিকে জয় করতে পারতে — আর ধর্মচক্ষু যে অমরত্বকে অবলোকন করেন, তাতে নিবেশিত হতে পারতে, সেই অমরত্ব, যাকে এতকাল ধরে তুচ্ছজ্ঞান করে এসেছ, যাকে এতকাল ধরে ভেবে এসেছ অবাস্তব, হাস্যকর, তোমাদের সদাব্যস্ত জীবনে যার কোন জায়গা নেই, অথচ যাকে এই এখন উপলব্ধি করছ যে, এ-ই সত্য, বাকী সমস্ত কিছু পুতুল-নাচ, বুদ্ধ-পর্বতে শুধু ওঠা আর নামা, তখন দেখতে আনন্দ, কোথাও কোন ব্যর্থতার ভয় থাকত না, হেরে যাবার প্রশ্ন উঠত না, পরম সৎ আলোকপ্রাপ্তিতে সত্যিই কোন আর ভয়, কোন দ্বিধা থাকত না আনন্দ।”
সহসা সকলের মনে হল জেতবনে সমস্ত বৃক্ষরাজি, জেতবনের সরোবর তটে সকল তরঙ্গ হতে যেন ধর্মের সঙ্গীত উদ্গীত হল, কে যেন তাদের ওপর যেন উজ্জ্বল আলোর জালিকা বিছিয়ে দিলেন। এমন অপার্থিব সৌন্দর্য ভক্তগণ এর পূর্বে কখনো প্রত্যক্ষ করেন নি। সকলে নীরব শ্রদ্ধায় চেয়ে রইলেন। কিছু না বুঝতে পেরেই তাঁরা রত্ন-সমাধির তূরীয় অবস্থায় প্রবেশ করলেন, অস্যার্থ, সকলের অন্তরে একযোগে অতীন্দ্রিয় তীব্র এক নীরবতার “গর্জন” যেন ধ্বনিত হল, সেই বারোশ’ তেত্রিশজন মানুষের উপরে লাল নীল, হলুদ শ্বেত — নীরব ধারায় যেন অযুত পুষ্পদলের ধারাস্নান হল, সে শতদল স্বর্গীয় শূন্যতায় রঙে রঙে মিলে মিশে একাকার। শুধু তাই নয়, তাঁদের মনে স্বহা-বিধৃত পৃথিবীর যে পর্বত, সমুদ্র, নদী-জঙ্গলের ভিন্নতার প্রকারভেদী ধারণা ছিল, সব যেন কোথায় মিলে মিশে এক হয়ে, কোথায় তারা লীন হয়ে গেল, পড়ে রইল শুধু আদি মহাবিশ্বের পুষ্পখচিত একমাত্রিকতা। আর তার গহ্বরের মাঝখানে তাঁরা পদ্মাসনে উপবিষ্ট ভগবান তথাগতের রূপ প্রত্যক্ষ করলেন, তথাগত, যিনি তথতা, যিনি এ জগতের মণি, এ জগতের স্তম্ভ!
দ্বাদশ অধ্যায়
তখন মঞ্জুশ্রী ভগবান বুদ্ধদেবকে সম্বোধন করে বললেন, “পরমারাধ্য ভগবন! প্রভু যখনই স্বর্গ হতে জন্ম-জন্মান্তরের দুঃখী মর্ত্যজগতে অবতরণ করেছেন, তখনই তিনি আমাদের তাঁর আশ্চর্য আলোকোজ্জ্বল শিক্ষায় আমাদের ধন্য করেছেন। তাঁর এই শিক্ষা আমরা সর্বাগ্রে আমাদের কর্ণে শ্রবণ করি, তথাপি যখন সেই শিক্ষা আমরা সর্বান্তকরণে উপলব্ধি করতে সক্ষম হই, তখনি তাকে আমরা তূরীয় শ্রবণক্ষমতাবলে আত্তীকৃত করতে পারি। অতএব নব্য সাধকদের কাছে অতীন্দ্রিয় শ্রবণবোধকে জাগ্রত করার বিশেষ তাৎপর্য আছে। সাধকের মনে সমাধি অবস্থা প্রাপ্তির যাচ্ঞা যখন গভীর হবে, তখন সে তাকে তার শ্রবণের অতীন্দ্রিয় ক্ষমতাবলে আয়ত্ত করতে সক্ষম হবে। প্রথমদিকে, কখনো কখনো, কোন বদ্ধ কক্ষে, কি বায়ুস্তব্ধ মধ্যরাতে যখন চরাচর নিদ্রামগ্ন, যখন চারিদিকের নৈঃশব্দে কান ঢেকেছে, তখন নব্য সাধক পরম সৎ-এর একান্ত শব্দে মনোনিবেশ করতে পারবেন, সেই শব্দ, যা সমস্ত শব্দের অনুপস্থিতি, অতীন্দ্রিয় পরম শূন্যতার শ্রুতি। আর তৎক্ষণাৎ তিনি এই অক্ষয় শ্রুতিকে উপলব্ধি করবেন যা তাঁর আপন অমৃত, অ-পুনর্জন্মিত, সৎচিতে অনাদি অনন্তকাল ধরে হয়ে চলেছে । হে ভগবন, সেই অপার স্তব্ধতায় তিনি বয়ে চলা শিক্ষাকে শ্রবণ করবেন। অতঃপর, তাকে তিনি সর্বত্র অবলোকন করবেন।
“অগণিত কল্প-ধরে — গঙ্গানদীর অযুত বালুকারাশির নয় অগণিত কল্প ধরে — অবলোকিতেশ্বর বুদ্ধ, যিনি সকলের প্রার্থনা শোনেন ও ইচ্ছাপূরণকরেন, সেই পরম কারুণিক বোধিসত্ত্ব, মহাবিশ্বের দশদিকে সর্ব বুদ্ধ-জগতে তাঁর নির্বাক পুণ্য শিক্ষার প্রকাশ করেছেন ও মুক্ত, নির্ভীক অনন্ত তূরীয় ক্ষমতাবলে সকল চেতন প্রাণীগণকে দাসত্ব ও দুঃখভোগ হতে নিবৃত্তি দানের শপথ গ্রহণ করেছেন। অবলোকিতেশ্বরের সেই তূরীয় শব্দ কি অপার্থিব সুমধুর ! সে এক ঐশ্বরিক শব্দ! সেই শব্দ অন্তর্মুখী সমুদ্রের ঢেউ-এর শব্দ। সকল চেতন প্রাণী যাঁরা আকুল হয়ে সাহায্যের প্রার্থনা করছে, তাদের কাছে এ নাদ শান্তি ও মুক্তি বয়ে আনে; নির্বাণের শান্তির যাঁরা প্রার্থনা করেন, তাঁদের কাছে এ এক অক্ষয় বোধ নিয়ে আসে।
“এই এখন, যখন ভগবান তথাগতের কাছে আমার আহ্বান নিবেদন করছি, তিনি, এই একই সময়ে, অবলোকিতেশ্বরের তূরীয় সংগীত শ্রবণ করছেন।
ঠিক যেমন, আমরা যখন একাকী ধ্যানমগ্ন হয়ে বসি, আমাদের কানে বাজনার দ্রিমি দ্রিমি ভেসে আসে, আর তখন মন যদি সে শব্দ শুনে, অবিচল শান্ত থাকে, সেই হল যথার্থ, সম্যক সহন।
“শরীর কোন কিছুর সংস্পর্শে এলে ধারণার উদয় হয়, চোখের দৃষ্টি বস্তুর অস্বচ্ছতা দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়, ঘ্রাণ ও স্বাদেরও ওই, কিন্তু মস্তিষ্ক-মনের ব্যাপারটি অন্যরকম। চিন্তার উদয় হয়, চিন্তা একে অপরের সঙ্গে মেশে, বয়ে চলে। দূর থেকে যে শব্দ ভেসে আসে, আর পাশের ঘর থেকে যে শব্দ ভেসে আসে সে উভয়কেই শোনে। অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের সেই সূক্ষ্ম ক্ষমতা নেই, শ্রবণ চরিত্রগত দিক থেকে দেখলে মাধ্যম হিসেবে সৎচিৎ।
“শব্দের চেতনা, সে কি নিঃশব্দে, কি জঙ্গম অবস্থায়, উপলব্ধি করা যায়। সে অস্তিত্ব থেকে অনস্তিত্বে বিচরণ করে। যখন কোন শব্দ থাকে না, বলা হয় শ্রবণ নেই, কিন্তু তার মানে এই নয় যে শ্রবণ হারিয়ে গেছে। সত্যি! যখন কোন শব্দ নেই কোথাও, তখন শ্রুতি প্রখর, আর যখন চারিদিক সশব্দ, শ্রবণের ক্ষমতা সবচেয়ে কম। যে সাধক আবির্ভাব আর অন্তর্ধানের এই মায়ার খেলা থেকে মুক্ত হয়েছেন, যথা, মৃত্যু আর পুনর্জন্মের থেকেও মুক্ত, তিনি যথার্থ অমরত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন।
“স্বপ্নেও, যখন সমস্ত চিন্তা স্তব্ধ হয়ে যায়, তখনো শোনার ক্ষমতা সদাজাগ্রত থাকে। এ যেন সম্বোধির আরশি, যে চিন্তন মনেরও তূরীয়, কেননা সে শরীর ও মনের চেতনেরও উর্দ্ধে বিচরণ করে। এই স্বহা জগতে, অন্তর্নিহিত, তূরীয় নাদ হয়ত সর্বত্রব্যাপী, তথাপি চেতন প্রাণীকূল তাঁদের অন্তর্নিহিত শ্রুতি বিষয়ে সচরাচর অচেতন। শব্দ যখন শ্রুতিমধুর কি কটু হয়, তখনই তাঁরা সংবেদনা জ্ঞাপন করেন।
“আনন্দের স্মৃতি যদিও প্রখর, তবু সে কুপথে যাওয়া থেকে নিজেকে এড়াতে পারেনি। সে বেচারী যেন এক নিষ্ঠুর সমুদ্রে ভেসে গেছে। যদি সে চিন্তার স্রোতে ভাসা থেকে মন নিবৃত্ত করতে পারে, তবে সে শীঘ্রই তন্মাত্র মনের প্রজ্ঞা ফিরে পাবে। আনন্দ! আমার কথা শোন! আমি সদা সর্বদা ভগবান বুদ্ধের বাণীর শরণ নিয়েছি, যেন তিনি আমার কাছে অনির্বচনীয় রত্ন-সমাধির ধর্ম তত্ত্বের প্রকাশ করেন। আনন্দ! তুমি কামনা-বাসনা রহিত না হয়ে, তোমার হৃদয়-দৌর্বল্য-কলুষতা-মত্ততা থেকে মুক্ত না হয়ে তুমি বুদ্ধ-জগতের গুপ্ত-রহস্যের সন্ধান করেছিলে। যার ফলে তোমার স্মৃতিতে বৈষয়িক জগতের অগাধ জ্ঞান অর্জন করেছ আর ভুলভ্রান্তির এক মিনার গড়ে তুলেছ।
“তুমি ভগবান বুদ্ধের বাণী মুখস্ত করে ধর্মের শিক্ষালাভ করেছ। তোমার আপন মনে অন্তর্নিহিত যে ধর্মের বাণী, কেন তার প্রতি মনোযোগ দিয়ে সেই বাণীকে নিজের জীবনে প্রতিফলিত করে শেখ নি? তূরীয় শ্রবণের যে অবলোকন তা তোমার আপন ইচ্ছাধীন কোন স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় হয় নি যে। হয়ত কখনো তুমি যখন তূরীয় শ্রবণের বিষয়টি চিন্তা করে দেখছিলে, তখন বাইরে থেকে অন্য আরেকটি কোন শব্দ হল, অমনি তোমার মন অন্যদিকে চলে গেল, তোমার মন বিব্রত হল, দ্বিধাবিভক্ত হল। যেইমাত্র তুমি আর সমস্ত শব্দ অগ্রাহ্য করতে পারবে, এমনকি তূরীয় নাদের যে ধারণা, তাও তোমার কাছে নিঃশেষিত হবে, তুমি তোমার অন্তর্নিহিত শ্রবণক্ষমতাকে বুঝতে শিখবে।
“যেই মুহুর্তে তোমার এই শ্রবণের সংবেদনা তার মূল সূত্রে ফিরে যাবে, যে মুহুর্তে তুমি তার অসারতা অনুধাবন করতে পারবে, মন তৎক্ষণাৎ সমস্ত সংবেদী ইন্দ্রিয়ের অসারতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে। সঙ্গে সঙ্গে দেখার, শোনার, আঘ্রাণের, স্বাদের, স্পর্শের, চিন্তার দাসত্ব থেকে তোমার মুক্তি হবে। মুক্তি হবেই, কেননা এরা সব একই রকমের মায়াবী, অসার। অস্তিত্বের তিন মহাজগৎকে দেখবে তারা যেমন, তেমন ভাবে, যেন আকাশে পুষ্পনিচয়।
“তারপর তোমার যে মুহুর্তে শ্রবণের মিথ্যা মায়া হতে মুক্তি হবে, তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যাপারও অপসৃত হবে, তোমার সহজাত তন্মাত্র মন হয়ে উঠবে সদসৎ। আপন হতে তার অন্তর্নিহিত ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ পাবে সর্বত্র, ও তুমি যখন ধ্যানের প্রশান্তিতে বসবে, তোমার মন পরম আকাশে স্থির হয়ে মিলবে।
“আনন্দ! তুমি পুনরায় যখন এই মরজগতে ফেরত আসবে, তখন তোমার মনে হবে সমস্ত কিছু স্বপ্নবৎ। প্রকৃতি (পচিতি) নামে নারীর সঙ্গে তোমার অভিজ্ঞতা মনে হবে স্বপ্নের মতন, তোমার শরীরীবোধ হারিয়ে যাবে। সকল মানুষ নারী কি পুরুষকে দেখে মনে হবে এরা যেন কোন এক অদৃশ্য জাদুকরের হাতের পুতুল, কিসের ইশারায় তাদের জীবন চলছে। প্রতিটি মানুষকে মনে হবে যেন একেকটি কলের পুতুল, আপন খেয়ালে নিজে নিজেই বেজে চলছে, আর তারপর কলের পুতুল যেমন, এরাও তেমন। যেইমাত্র দম ফুরিয়ে যাবে, শুধু যে সে থেমে যাবে তাই নয়, তার অস্তিত্বও বিলীন হবে।
“তো এই হল ষড়েন্দ্রিয়ের খেলা, এরা মূলত এক অভিন্ন শক্তির ওপর নির্ভরশীল, অথচ অজ্ঞানতাবশত ছ’টি প্রায়-স্বাধীন অংশে বিভক্ত হয়ে আছে। যেদিন একটি অঙ্গ তার উৎসে ফিরে যাবে, সেদিন আর পাঁচটা অঙ্গও একইভাবে তাদের কাজ সমাপ্ত করে ফিরে যাবে। জগতের সকল কলুষতা দূর করতে একটিমাত্র সৎচিন্তাই যথেষ্ট, তাতেই তোমার সম্যক বোধি অর্জন হবে। তার পরেও যদি মনে কলুষতা রয়ে যায়, মনে প্রাণে তথাগতের সম্যক আলোকপ্রাপ্তির ধ্যান কোর।
“এই মহাসভার সমস্ত ভ্রাতাদের বলছি, আর হ্যাঁ আনন্দ তোমাকেও, তোমরা তোমাদের বহির্জাগতিক চেতনাকে অন্তর্মুখী করে তোল; তোমাদের পরমানন্দ মনকে অনুধাবন কর, কেননা যেইমাত্র তাকে উপলব্ধি করবে, তৎক্ষণাৎ তোমাদের পরমানন্দ আলোক প্রাপ্ত হবে।
“নির্বাণের এই একমাত্র পথ; আদিকাল হতে সকল তথাগতগণ এই পথই অবলম্বন করেছেন। তদুপরি, ইহকাল ও ভাবীকালের সমস্ত বোধিসত্ত্ব-মহাসত্ত্বগণ পরম আলোকত্বলাভ করার অভিপ্রায়ে এই পথই অবলম্বন করেন। বহুকাল পূর্বে এই স্বর্ণপথে অবলোকিতেশ্বর অগ্রসর হয়েছিলেন, আবার এযুগে আমিও তাঁদেরই একজন।
“প্রভু জানতে চেয়েছেন কি প্রকারে নির্বাণলাভের এই মহৎ দ্রুতগামী পন্থা আমরা অবলম্বন করেছি। আমি নিজে জানি অবলোকিতেশ্বর কি উপায়ে এ পথ ধরেছিলেন ও এই মার্গই সবচেয়ে দ্রুতগামী, কেননা আর সব পন্থা অবলম্বন করতে গেলে ভগবান বুদ্ধের তূরীয় শক্তিবল ও তাঁর সাহায্য প্রয়োজন। এমনকি কেউ যদি তার সমস্ত পার্থিব যোগাযোগ ছিন্ন করে, তাহলেও তার পক্ষে সব রকম আচার আচরণ পালন করা হয়ত সম্ভব হবে না। বয়োজ্যেষ্ঠ, কনিষ্ঠ সাধকদের জন্য নানান পন্থা বিদ্যমান, তবে সর্বসাধারণের জন্য এইটিই সবচেয়ে সহজ উপায় — মনকে শ্রবণেন্দ্রিয়ে স্থিত ও নিবেশিত করে এই ধর্মদ্বারপথে অন্তর্মুখী করে তোলা, যাতে তন্মাত্র মনের তূরীয় নাদ সে শ্রবণ করতে সক্ষম হয়। এ পথ অবলম্বন করাই সবচেয়ে সহজ ও বুদ্ধিমানের কাজ হবে।
“হে প্রভু! ভগবান তথাগতের অন্তর্নিহিত গর্ভের সুমুখে আমি প্রণিপাত করি, যিনি অনির্বচনীয়, যিনি অনুপম, যিনি সর্বংসিদ্ধ, যিনি সর্ব প্রকার কলুষতামুক্ত, আমি সেই ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করি তিনি যেন ভবিষ্যতের সর্বমানবের হিতার্থে তাঁর অপার করুণা প্রদান করেন, আমি যেন ইহকল্পে আনন্দ ও আর সকল চেতন প্রাণীগণকে কিভাবে এই আশ্চর্য ধর্মদ্বার অতিক্রম করে আপন মনের অভ্যন্তরে রচিত তূরীয় নিনাদ উপলব্ধি করতে হয় তার শিক্ষা প্রদান করতে পারি। যদি কোন সাধক সহজবোধ্য উপায়ে তূরীয় শ্রবণলাভের উদ্দেশ্যে কেবলমাত্র ধ্যানে তার মন সংযোগ করতে পারে, তার অন্যান্য ইন্দ্রিয়ও কালক্রমে ঐকতানে সমবেত হবে। এইভাবে, অন্তরনিহিত শ্রবণবলে সে তার পরম তন্মাত্র মনকে উপলব্ধি করতে পারবে।“
তখন আনন্দ ও সেই মহাসভায় অন্যান্য যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা কায়-মনে পবিত্র হলেন, তাঁদের এই বোধ হল। তাঁরা ভগবান বুদ্ধের বোধির স্বরূপ গভীরভাবে উপলব্ধি করলেন, এ বিষয়ে তাঁদের স্বচ্ছ জ্ঞান অর্জন হল। তারা চূড়ান্ত সমাধি ধ্যানের পরমানন্দ অনুভব করলেন। অভিজ্ঞ বণিক যেমন ব্যবসার উদ্দেশ্যে দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে দূরদেশ পাড়ি দেয়, তাঁদেরও তেমন ধর্মের পথে প্রত্যয় দৃঢ় হল। তাঁরা ধর্মপথে যাতায়াতের মার্গ-নির্দেশিকা পেলেন। এই মহাসভার সকল ভক্তশিষ্যরা তাঁদের আপন আপন তন্মাত্র মন উপলব্ধি করলেন, এবং প্রতিজ্ঞা করলেন অতঃপর, তাঁরা ইহজগতের সাংসারিক জটিলতা, সাংসারিক মলিনতা থেকে মুক্ত হয়ে সদাসর্বদা ধর্ম-চক্ষুর পরম ঔজ্জ্বল্যে নিত্যদিন অতিবাহিত করবেন।
তখন ভগবান বুদ্ধদেব, যাঁরা ইহজীবনে বোধিসত্ত্ব-মহাসত্ত্বের স্তর অর্জন করতে চান, তাঁদের জন্য নিম্নলিখিত তিনটি আদেশ প্রদান করে সভা সমাপ্ত করলেন:
১। মন নিবেশ করতে হবে
২। উপদেশ পালন করতে হবে
৩। ধ্যানাভ্যাস করতে হবে
“মন নিবেশ করতে হবে” অর্থে সদাসর্বদা সদবুদ্ধি পালন করতে হবে, যে যেমন তাকে তেমন করেই দেখতে হবে, “কে কি” তার চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে যেন না ঠকে যেতে হয়, ও কোন কিছুকে যেন আঁকড়ে থাকতে না হয়। এ যেন একজন মানুষ হঠাৎ করে মধ্যরাত্রে পরম সত্য দর্শণ করে জেগে উঠলেন, তখন তাঁর ভারি ভাল লাগল, মাথা নাড়িয়ে বলে উঠলেন, “সবকিছুই সেই এক”। স্বপ্নহীন নিদ্রা থেকে তিনি অকলঙ্ক একত্রিত এক জগতে জেগে উঠলেন,যে জগতে আগে “নির্ভুল একত্রীকরণ” বলে কিছুই ছিল না, আর যেন তিনি তাবৎ সৃষ্ট বস্তুকে এক মহাশূন্যতায় অবলোকন করলেন, এক পরম আদি সত্যের শূন্যতার মহাসমুদ্রে তাদের আপাত প্রকাশ ঘটেছে, তারা কেউ আলাদা কিছু নয়, তারা সবাই এক হয়ে গেছে, এক বৃহৎত্বে।
“উপদেশ পালন করতে হবে” অর্থে সৎ জীবন যাপনের চারটি নিয়ম কঠোরভাবে পালন করতে হবে। এ করতে পারলে সাধক মাদকতা থেকে মুক্ত হবেন, দুঃখভোগ থেকে তাঁর মুক্তি ঘটবে, অতএব সংসার থেকে তিনি মুক্ত হবেন, এবং তাবৎ সাংসারিক ভুয়োদর্শণ, মৃত্যু-পুনর্জন্মবোধ থেকেও তাঁর মুক্তি হবে। এই উপদেশাবলী সমগ্র জীবজগতের প্রতি করুণাবশত, আত্মশুদ্ধ, “হে সাধুগণ! এই তরীকে ভারমুক্ত করুন। যেইমাত্র এ তরী ভারমুক্ত হবে, সে দ্রুতগমন করতে সক্ষম হবে, আসক্তি-ঘৃণা উভয়কেই পরিহার করে আপনারাও নির্বাণ লাভ করবেন।”
এই চারটি নিয়ম হল:
১। জেগে ওঠ, কামভাব নিবৃত্ত কর, কামভাব, কামোন্মত্ততা, কামাসক্তি থেকে যুদ্ধংদেহি ভাব জেগে ওঠে, আর সেখানেই দুঃখবোধের উৎপত্তি
২। জেগে ওঠ, অপরের প্রতি নিষ্ঠুরতা পরিহার কর, নিষ্ঠুরতা জ্ঞানীজীবনের হন্তারক
৩। জেগে ওঠ, কামনা-বাসনা আর তস্করবৃত্তির নিবৃত্তি কর, তোমার শরীরকে কেবল তোমার নিজের শরীর জ্ঞান না করে অন্য সমস্ত চেতন প্রাণের সঙ্গে একাত্ম কর
৪। জেগে ওঠ, শঠতা, কোপনতা, মিথ্যা আচরণ বন্ধ কর, জীবনে যেন কোন মিথ্যা কিছু না থাকে, ফেটে যাওয়া শিশিরবিন্দুতে কি কিছু গোপন থাকে?
“ধ্যান অভ্যাস কর” অর্থে প্রতিদিন নিয়ম করে ধ্যান করা যাতে সমাধি ধ্যানের অবস্থা ও সমাপত্তির আধ্যাত্মিক ক্ষমতা অর্জন করতে পার, পুরাকাল ও ভাবীকালের মহৎ জ্ঞানীজনেরা যে কথা বলে গেছেন ও বলবেন, এতে সাংসারিক জীবন হতে উদ্ধারের অবস্থাপ্রাপ্ত হবে।
ভগবান বুদ্ধদেব যখন সুরঙ্গমা সূত্রে লিখিত এই উপদেশ সমাপ্ত করলেন, তখন সমবেত ভিক্ষু-ভিক্ষুণী, স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে সকল গৃহী ভক্তগণ, মহাপণ্ডিত যাঁরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, অপরাপর বুদ্ধগণ, সাধুগণ, অর্হৎগণ, সদ্য-শিষ্যত্ব-গ্রহণকারী মহাশক্তিধর রাজন্যবর্গ — এঁদের সকলের হৃদয়ে অপার আনন্দ বোধ হল। হৃষ্টচিত্তে সকলে ভগবান বুদ্ধদেবকে আন্তরিক বিনম্র শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে প্রস্থান করলেন।
ত্রয়োদশ অধ্যায়
দেবদত্ত পরবর্তীকালে কুখ্যাত হয়েছিল। সে নিজের মত করে অপর একটি সম্প্রদায় তৈরী করার চেষ্টা করে; সেই সম্প্রদায়ের নিয়ম কানুন বুদ্ধদেব যে সমস্ত নিয়মের কথা বলতেন তার থেকে আরো কড়া। দেবদত্ত নানান রকমের জাদুবিদ্যা, বিশেষ করে সম্মোহনী বিদ্যা, আয়ত্ত করেছিল। এসব সে মহারাজ বিম্বিসারের পুত্র যুবরাজ অজাতশত্রুর ওপর প্রয়োগ করে, এই করে অজাতশত্রু বিম্বিসারকে হত্যা করার সংকল্প করেছিলেন। মগধের রাজা হয়ে অজাতশত্রু দেবদত্তের জন্য একটি মঠ তৈরী করে দিয়েছিলেন। দেবদত্ত নতুন রাজার ওপর প্রভাব খাটিয়ে রাজাকে প্ররোচিত করেছিল যে গৌতমকে সংঘের অধ্যক্ষ পদ থেকে সরিয়ে দিতে, এই বলে যে মহৎ জনকে বার্ধক্য গ্রাস করেছে।
বুদ্ধদেব দেবদত্তের এই সমস্ত অনাচার উপেক্ষা করে বললেন, “ও মহাসমুদ্রে এক ঘড়া বিষ ঢেলে ভাবছে সমস্ত সাগর বুঝি বিষিয়ে দেবে।”
দেবদত্ত দেখলে যে পরমারাধ্যের কাছ থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেবার যে ফন্দি সে এঁটেছিল, তাতে বিশেষ কাজ হল না। সে উপলব্ধিও করেনি যে পরমারাধ্য জন ক্ষমতা কি দৌর্বল্য, এই নিয়ে বিন্দুমাত্র বিচলিত নন। তখন দেবদত্ত স্থির করল তাঁকে হত্যা করবে। এই মনে করে একদল দস্যুকে পাঠাল ভগবনকে হত্যা করতে, কিন্তু তারা তাঁর দর্শণ পাওয়ামাত্র, তাঁর প্রেমময় রূপ, তাঁর মুখনিঃসৃত বাণী শুনে এমনই মোহিত হয়ে গেল যে উল্টে তাঁর শরণ নিল। গৃধ্রকূট পাহাড় থেকে একটা মস্ত পাথর মহাগুরুর দিকে ছুঁড়ে দেওয়া হল, কিন্তু তা নিমেষে দুটুকরো হয়ে গেল, তাতেও তাঁর কোন ক্ষতি হল না। একবার মহৎ জন যে সময় রাজপথ ধরে যাবেন, সেই সময়ে একটি মত্ত হস্তীকে রাজপথে ছেড়ে দেওয়া হল । বুদ্ধদেবের দর্শণ মাত্রই প্রকাণ্ড ভয়ঙ্কর প্রাণীটি তাঁর সামনে শান্ত হয়ে বসে রইল। আসিসির সেন্ট ফ্রান্সিসের মতন, বুদ্ধদেবেরও পশুদের ওপর আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল। ভগবন সেই প্রকাণ্ড পশুটির মস্তকে তাঁর পদ্ম-হস্ত রাখলেন, চাঁদ যেমন চলন্ত মেঘের ওপর আলোক বর্ষণ করে, সেই রকম বুদ্ধদেব স্নেহভরে তাকে বললেন,
“ছোট্ট হাতি কাঁটাবন ভেঙে ফেলে, তাকে আদর করলে জানি যে সে মানুষের উপকারে লাগে। কিন্তু যে মেঘ এই হস্তীর বার্ধক্যের যন্ত্রণা দূর করে, তার ভার কেউ সইতে পারে না। ওগো তুমি! দুঃখের পাঁকে নিমজ্জিত। এখনও যদি না ত্যাগ কর, লোভ, ক্রোধ, মায়া যে ক্রমশ বাড়তেই থাকবে।”
“ধনপালক নামে হাতিটি, দুর্গন্ধে কাদায় ভেসে যাচ্ছে তার কপাল, তাকে ধরে রাখা দায, আবদ্ধ অবস্থায় সে একটি দানাও মুখে তুলল না, হাতিটি হস্তীবনে যেতে চায়” (ধম্মপদ)
শিষ্যদের বুদ্ধদেব বললেন, “যুদ্ধে হস্তী যেমন শর সহ্য করে, সেই রকম আমিও নীরবে বহু অত্যাচার সহ্য করেছি। এই পৃথিবীর স্বভাব অতি কুটিল। মানুষ হাতীকে পোষ মানিয়ে তাকে যুদ্ধে নিয়ে যায়; রাজা পোষা হাতীর পিঠে চড়েন; অথচ দেখ যে পোষ মেনেছে, তারই সবথেকে বেশী শক্তি; তবু সে নীরবে কত না অত্যাচার সহ্য করে। পোষ মানলে অশ্বতরেরাও কাজে আসে, সিন্ধু প্রদেশের সুদর্শন অশ্বেরাও, এমনকি বৃহৎ দন্তবিশিষ্ট হস্তীদলও তাই; তবে যে মানুষ নিজেকে পোষ মানাতে পারেন তিনি সকলের চেয়ে মহৎ।
কুচক্রী দেবদত্ত আর তাঁর সুপুত্র রাহুল, এই দুজনের প্রতি বুদ্ধদেব সম-মনস্ক ছিলেন। সংঘের অন্যান্য সদস্যরা দেবদত্তকে নিতান্ত “মূর্খ” বলে জ্ঞান করতেন। প্রত্যেক দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন ভিক্ষু জানতেন যে একদিন দেবদত্তও বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হবে, কেননা অনুত্তর-সম্যক-সম্বোধি অনুযায়ী সকল বস্তই যে এক অভিন্ন!
রাজা অজাতশত্রু যখন দেখলেন যে দেবদত্ত নামে এই মূর্খ বীরপুরুষটিকে দিয়ে আর কোন কাজ হবার নয়, তখন তাঁর ভারি অনুতাপ হল। তখন তিনি পরমারাধ্য জনের কাছে গিয়ে পরিতাপ করলেন, মুক্তির উপায় জানতে চাইলেন।
বুদ্ধদেবের বিশাল জনপ্রিয়তা, ও সাধারণ মানুষ বুদ্ধদেবের শিষ্যদের কত রকম যে উপঢৌকন দিতেন তার ইয়ত্তা নেই, এই সব দেখে সমাজের কিছু মাতব্বর শ্রেণীর মানুষের মনে ভারি হিংসা হত। এই মাতব্বররা নানারকম ভাবে চেষ্টা করত কি করে পরমজনকে কালিমালিপ্ত করা যায়, কিভাবে বুদ্ধদেবকে লোকের চোখে ছোট করা যায়। একবার চিন্চা নামে এক নকল সাধ্বী সভার সকলের সামনে পরমারাধ্য জনের নামে ব্যভিচারের অভিযোগ আনবে মনস্থ করল। তবে তার এই মিথ্যা ফন্দি কারো কাছে গোপন রইল না। আরেকবার, কতিপয় বিক্ষুব্ধ লোক স্থির করল বুদ্ধদেবের নামে অপবাদ দেবে। সুন্দরী নামে এক মহিলার সঙ্গে যোগাযোগ করে তাকে বলল কানাঘুষো ছড়াতে যে সে নাকি রাতে বুদ্ধদেবের শয়ন কক্ষে যায়। সেই অপবাদও কোন কাজে এল না, ইতিমধ্যে কুচক্রীরা একদল মাতালের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে সুন্দরীকে মেরে তার লাশ জেতবনের কাছে একটি ঝোপের মধ্যে ফেলে দিল। বিক্ষুব্ধরা ব্যাপারটাকে সাজাতে চাইল যেন বুদ্ধদেবের শিষ্যরা এই কীর্তি করেছে, কিন্তু সাজাতে গিয়ে গোলমাল করে বসল। যাই হোক, বুদ্ধদেবের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হোক, এই রকম একটা কলরোল শোনা গেল। এদিকে মত্ত অবস্থায় হত্যাকারীরা নিজেরা নিজেদের মধ্যে এমন মারামারি শুরু করল যে অচিরেই ষড়যন্ত্রের ব্যাপারটি জানাজানি হয়ে গেল। তাদের রাজার কাছে ধরে আনা হলে তারা নিজেরাই করল আসল ঘটনা স্বীকার করে তাদের যারা প্ররোচিত করেছিল, নিয়োজিত করেছিল, তাদের নামধাম ফাঁস করে দিল। আরেকবারের কথা। নরাসু লিখছেন, “বিক্ষুব্ধরা শ্রীগুপ্তকে খুব করে উসকাতে লাগল প্রভুর খাবারে বিষ মিশিয়ে, তারপর তাঁকে বিপথে নিয়ে গিয়ে আগুনে ছুঁড়ে ফেলে তাঁর প্রাণহরণ করার জন্য। কিন্তু উলটে পরম করুনাঘন বুদ্ধদেবই শ্রীগুপ্তকে বাঁচালেন।“
প্রভুর আন্তরিকতায়, সহজ সারল্যে অভিভূত হয়ে আরো বহু শিষ্য সংঘে যোগ দিলেন। যীশুখ্রিস্টের যেমন ১২ জন, তেমনি খ্রীস্টের জন্মের ৫০০ বছর আগে বুদ্ধদেবেরও ১২ জন শিষ্য ছিলেন। তাঁদের সম্বন্ধে বুদ্ধদেব বলতেন, “আমার এই ধর্মে ১২ জন শিষ্য, যাঁরা নিজেরা এতটাই ভাল যে, এঁদের আপন শক্তিতে এঁরা এ জগৎকে ত্রাণ করবেন, এঁদের মতন আর কাকেও পাওয়া যাবে না।”
একবার দক্ষিণ দেশে অবস্থানকালীন বুদ্ধদেব একনলা গ্রামে গিয়েছিলেন। সেখানে এক ধনী কৃষক ব্রাহ্মণ লাঠি হাতে তাঁর মাঠের শ্রমিকদের তদারকি করছিলেন, সে বেচারারা বলদদের সঙ্গে একযোগে খাটছিল। বুদ্ধদেব ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে কাছে এসে দাঁড়ালেন। কয়েকজন মজুরও, যারা মাঠে পরিশ্রম করছিল, বুদ্ধদেবকে দেখতে পেয়ে হাত জোড় করে এসে প্রণাম করল। ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক বুদ্ধদেব কে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে খেঁকিয়ে উঠলেন, “এই যে, হাঁ করে দাঁড়িয়ে কি দেখছেন? দেখুন আমি হাল চাষ করাই, করিয়ে তবে ভাত খাই। এই রকম হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকার চেয়ে ভাল হত আপনিও যদি চাষ বাস করতে শিখতেন, জানতেন, খেটে খেতেন!”
“হে ব্রাহ্মণ”, বুদ্ধদেব উত্তর দিলেন,”আমিও তো হলকর্ষণ করি, বীজ বপন করি, বীজ বপন, হলকর্ষণ করা হলে, তবেই অন্ন গ্রহণ করি।”
“কিন্তু” ব্রাহ্মণ বললেন, “আপনি যে কৃষক, তার প্রমাণ কি? কোথায় আপনার বলদ, কোথায়ই বা আপনার বীজ, আর কোথায়ই বা আপনার লাঙল?”
তখন মহাশিক্ষক উত্তর দিলেন, “যে বীজ আমি বপন করি তার নাম বিশ্বাস; ভক্তি সেই বারিধারা যা তাকে জলসিঞ্চন করে উর্বর করে; নম্রতা হল আমার হল; মন সে জোয়ালের বন্ধন, মনোনিবেশতা সে লাঙলের ফলা, সত্যকথন তাকে বেঁধে রাখে, নম্রতা তাকে বন্ধন থেকে মুক্ত করে। শক্তি আমার বলদ, আমার শ্রমিকের দল। এইভাবে কৃষিকাজ করি, ভ্রান্তি নামে আগাছা উপড়ে ফেলি। আমি নির্বাণরূপ পারমার্থিক ফল ফলাই, এই পরিশ্রমে জগতে দুঃখের অবসান হবে।”
এই কথা শুনে ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক নিজে হাতে একটি সোনার বাটিতে পায়েস ঢেলে বুদ্ধদেবকে অর্ঘ্য দিলেন, দিয়ে বললেন, “এই পায়সান্ন গ্রহণ করুন হে গৌতম। আপনি যথার্থই একজন কৃষক; কেননা আপনি যে কৃষিকাজ করেন তাতে অমরত্বের ফসল ফলে।”
লিচ্ছবির রাজকন্যাদের পরমজন বলেছিলেন, “প্রজ্ঞাবান হতে হলে “অহংবোধ” দূর করে দাও; “আমিত্বের চিন্তা সমস্ত সৎ উদ্দেশ্যকে কালিমালিপ্ত করে, ছাই যেমন আগুন ঢেকে রাখে, অথচ তার ওপরে হাঁটলে পা পুড়ে যায়।
“অহংকার আর উপেক্ষা আমাদের হৃদয়কেও ঢেকে রাখে, পুঞ্জীভূত মেঘমালা যেমন সূর্যকে আড়াল করে রাখে; অহংকার মনের বিনয়বোধকে নষ্ট করে সমূলে উৎপাটিত করে, অত্যন্ত দৃঢ়চেতা মানুষকেও দুঃখ গ্রাস করে।
“আমি বিজয়ীগণের মধ্যে বিজয়ী, তাই যে নিজেকে জয় করেছে, তার সঙ্গে আমার আত্মার মিলন।
“যার কাছে নিজেকে জয় করার বিষয়টি নেহাতই তুচ্ছ, মালিক হিসেবে সে নেহাতই অল্পবুদ্ধি। পার্থিব সৌন্দর্য, পারিবারিক সমৃদ্ধি, সুনাম, এসব তো চীরকাল থাকে না, থাকে না বলেই, যা জঙ্গম, তাতে কারো শান্তি হয় না।
“এই বোধ জন্মালেই “আমিত্বের” কামনা-বাসনা থেকে মুক্তিলাভ হয়, কেননা “আমিই শ্রেষ্ঠ”, এইরকম মিথ্যা ধারণা থেকে আরো চাই জাতীয় লোভের উৎপত্তি হয়, তারপর ত্রুটির মিথ্যা ধারণা থেকেও ক্রোধ আর হাহুতাশ, অথচ চরম উৎকর্ষতা আর নিজেকে ছোট করার বোধ যেদিন ধ্বংস হবে, সেদিন ক্রোধের বাসনারও নিবৃত্তি হবে।
“ক্রোধ! দেখ কেমন করে সে মানুষের সরল মুখচ্ছবিকে পালটে দেয়, কেমন করে সে সৌন্দর্যকে নষ্ট করে!”
সাপুড়ের বাঁশিতে মোহিত উজ্জ্বল-চর্ম সর্প যেমন জেগে ওঠে, পরমজনের কথা শুনে লিচ্ছবির যোদ্ধাদেরও ভারি উজ্জ্বল বোধ হল, অতঃপর তাঁরা তাঁদের নয়নাভিরাম উপত্যকায় সুখে শান্তিতে বসবাস করতে লাগলেন। একান্তে থেকে, শান্তিতে থেকেই তাঁদের আনন্দ, তাঁরা পারমার্থিক ধ্যান করতেন।
“সাধুগণ, বলুন দেখি, কোন সাধু গোসিংহম বনের শৌর্যবৃদ্ধি করেছেন?” গোসিংহম অরণ্যে সেদিন নির্মেঘ এক রাত, স্বর্গীয় পুষ্পশোভিত সে উদ্যানে সুগন্ধে চারিদিক ম’ম’, এমন সময় সারিপুত্র, মৌদ্গল্যায়ন, আনন্দ, অনুরুদ্ধ, রেবত, কশ্যপদের বুদ্ধদেব এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন। “জানেন? সেই সাধু, যিনি মাধুকরী-অন্তে, খাদ্যগ্রহণ করে, শরীর ঋজু রেখে হাঁটু মুড়ে ধ্যানে বসে প্রতিজ্ঞা করেন, “যতক্ষণ না কামনা-বাসনা থেকে মুক্তি হচ্ছে আমার, যতক্ষণ না আমার মন তামসিক বোধ থেকে না মুক্তি পাচ্ছে, ততক্ষণ এ স্থান থেকে উঠব না।” এই হল সেই সাচ্চা সাধু যে গোসিংহম বনের শৌর্য!”
সত্য — সে যে ধরিত্রী অপেক্ষা প্রাচীন, ইতিহাসের চেয়ে তার ওজন ভারী, রক্তপাতের চেয়ে ভয়ংকর তার নির্গমন, উপহাররূপে সে অন্নদানের চেয়ে মূল্যবান।
নির্মাণকায় বুদ্ধরূপে,অথচ আর পাঁচজন আত্মার মতই ঐশ্বরীয় ধরিত্রীতে, এই পৃথিবীর বুকে পথ হাঁটেন তিনি, তাঁর সেই পথ হাঁটার যখন অষ্টতিতম বছর, তখন একদিন তিনি বললেন, “আমার মুক্তির সময় সমাসন্ন, তিন মাস অতিক্রান্ত হলে, আমি নির্বাণলাভ করব।”
বৃক্ষতলে উপবেশিত তথাগত, তিনি তূরীয়বোধে ধ্যানস্থ, আপন ইচ্ছায় তাঁর প্রারব্ধ সময় পরিত্যাগ করতঃ অধ্যাত্ম যোগে জীবনের বাকী কয়েকটি দিন স্থির করলেন।
বুদ্ধদেব তাঁর তূরীয় ধ্যান থেকে উঠে জগতে একথা ঘোষণা করলেন,
“আমি সময় পরিত্যাগ করব স্থির করেছি:অতঃপর আমি বিশ্বাসের শক্তির ওপর নির্ভর করে বাকী জীবন অতিবাহিত করব; ভগ্নরথের প্রায় আমার দেহ স্থিত রবে, না-আসা, না-যাওয়া, স্বর্গ-মর্ত্য-নরক ত্রিভুবন হতে আমি মুক্ত, পক্ষীশাবক যেমন অণ্ড হতে নির্গত হয়, তদ্রূপ, আমি স্বাধীনভাবে চলে যাব, একাকী।
“আনন্দ! আমার জীবনান্তের আমি তিন মাস স্থির করেছি । বাকী জীবন আমি পরিত্যাগ করলাম। তাই ধরিত্রী কম্পমান।
আনন্দ রোদন করলেন, “রক্ষা করুন প্রভু! আমাদের করুণা করুন। এত শীঘ্র বিদায় নেবেন না”
পরমজন উত্তর দিলেন, “মানুষ যদি আপন প্রকৃতি জানত, তাহলে সে দুঃখে নিমজ্জিত হত না। সকল জীবিত বস্তুই ধ্বংসের নিয়মের অধীন; তোমাকে তো সহজ করে বলেইছি আনন্দ, সমস্ত “সংযুক্ত” বস্তুই কালের নিয়মে “বিযুক্ত” হবে।”
গহন অরণ্যে একাকী আনন্দ রোরুদ্যমান, পরম জন তাঁকে ডেকে মরমী সত্য শুধোলেন,
“আমাদের চারপাশে যা আছে, সব যদি রাখতে পারতুম, তাদের যদি বিচ্ছেদ না হত, তাদের যদি পরিবর্তন না হত, তাহলে তাই হত মুক্তি! সে কোথায় পাবে?
“সেই অনির্বচনীয়, যার নাগাল তোমরা পাবে, তার কথা আমি আগেও তোমাদের বলেছি, শেষ পর্যন্ত তার কথাই বলে যাব।
“প্রেম জেগে থাকে সমস্ত বস্তুর অন্তঃস্থলে, সমস্ত বস্তুই এক বস্তু। স্বহা! আমার দিন শেষ হয়ে এসেছে, আমি এবার বিশ্রাম নেব। যা করার ছিল,বহুকাল আগে করা হয়ে গেছে।
“পূর্ণজ্ঞানী পূর্ণকারুণিক সকল তথাগত, সুগত, বুদ্ধ, যাঁরা এই অলৌকিক বাক্যে বোধিপ্রাপ্ত হয়েছেন, হয়ে চলেছেন, ও হবেন, তাঁদের প্রণাম।
“আনন্দ, শান্ত চিত্তে একটি নির্জন স্থানে আসন বিছাও, অন্যের চিন্তাধারায় প্রভাবিত হয়ো না, অন্যের অজ্ঞানতাবশতঃ চিন্তাধারায় তাল মিলিও না, একলা চল, একাকীত্বকেই তোমার স্বর্গ মেনো, শুভ চেতনার, শান্ত আঁখির সংঘ তোমার সাথে সাথী হবে।
“মন সতত বস্তুর আবির্ভাব, স্থিতি, আর লয়ের সঙ্গেই পরিচিত, বোঝে যে বস্তু একে অপরকে অনুসরণ করে, জানে যে কারো কোন স্থিতি নেই। জ্ঞানীজন বোঝেন যে আমিত্বের কোন ভিত্তি নেই তাই।
“জন্মের পূর্বকালে জ্ঞানী মানুষের অবয়ব নিয়ে কিছুই করার নেই, অবয়ব নিয়ে এখনও তার কিছুই করার নেই, মৃত্যুর পরেও কিছুই করার থাকবে না। অবয়বের অস্তিত্ব অনস্তিত্বের কোন তফাত নেই, এই জ্ঞান হবার পরে সে কিরূপে মারা যায়?
“আনন্দ, দুঃখ কোর না। দেহের জন্মের পুনঃপৌনিকতার অবসান করাই আমার উদ্দেশ্য । সকল বস্তুই অস্থাবর, অলাভজনক, কণ্টকাকীর্ণ, সতত পরিবর্তনশীল, অথচ মানুষ নিয়ন্ত্রণবিমুখ, সকলেই তাদের দেহের, তাদের অবয়বের কারণে সতত দুঃখভোগ করে।
“সকল বস্তু, যা জাত, অপ্রবোধিত, তা একদিন না একদিন শেষ হবেই।”
“এ ধর্মকে গ্রহণ করতে শেখ, কেননা এ সত্য, এ আত্মবিকশিত।
বুদ্ধদেবের মরণেচ্ছার সংবাদ পেয়ে বৈশালীর লিচ্ছবিরা পরম আর্ত মনে দুঃখীত মুখে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। বুদ্ধদেব তাঁদের বললেন, “প্রাচীন যুগের ঋষিরাজগণ, বশিষ্ঠমুনি, মান্ধাত্রি, চক্রবর্তী রাজন্যবর্গ, অন্যান্যরা, তাঁদের মতন আরো সব, যাঁরা ঐশ্বরিক শক্তিতে বিরাজ করতেন, তাঁরা সবাই বহুকাল হল একে একে গত হয়েছেন, কেউ আজ আর বেঁচে নেই। চন্দ্র, সূর্য, শক্র স্বয়ং, তাঁর শত শত পরিচারকগণ, তাঁরাও সবাই গত। এমন কেউ নেই যে যুগ যুগান্ত ধরে বেঁচে থাকবে। পুরাকালের সকল বুদ্ধগণ, সংখ্যায় যাঁরা গঙ্গার বালুকারাশির ন্যায় অযুত, যাঁরা তাঁদের প্রজ্ঞায় জগৎ আলোকিত করেছেন, তাঁরাও সকলে প্রদীপের নির্বাপিত শিখার ন্যায় অস্তগত। সকল বুদ্ধগণ, যাঁরা অনাগত, তাঁরাও একই পথে গত হবেন; তবে আমার বেলা কেন শুধু অন্যথা?
“আমিও নির্বাণে অস্তমিত হব; অন্যদের যেমন মুক্তির পথে প্রস্তুত করা হয়েছে, তোমরাও পথ ধরে এগিয়ে যাবে, তোমরা বিশ্রামের পথ দেখালে বৈশালীর সকলে সুখী হবে।
“সত্যি কথা বলতে কি, পৃথিবীতে কোথাও প্রকৃত সাহায্য নেই, আমোদ করার জন্য ত্রিভুবনও যথেষ্ট নয়, কামনা বাসনাহীন হৃদয় গড়, দুঃখের পথ আটকাও।
“জীবনের দীর্ঘ এলোমেলো পথ চলা ছাড়ো এবার, উত্তর পথে চল, পায়ে পায়ে ক্রমশ উপরে উঠে যাওয়া পথ বেয়ে যে পথে পশ্চিম পাহাড়ে সূর্যের বাঁকে পথ বেঁকে গেছে, সে পথে চল যাই।“
মহাশিক্ষক তাঁর শেষ দীক্ষা-ভ্রমণে পাভা শহরে এলেন। সেখানে চুণ্ড নামে লৌহকারের গৃহে তিনি তাঁর শেষ আহার করলেন। পরমজন বুঝতে পেরেছিলেন যে চুণ্ড তাঁকে যে শূকরমাধ্ব নামে যে ছত্রাক-মিশ্রিত শূকর মাংস খেতে দিয়েছিল, তা খাবার উপযোগী ছিল না, তাঁর অনুগামীদের নিষেধ করলেন, বললেন স্পর্শ না করতে। বৌদ্ধ নিয়মানুসারে কোন ভক্ত কিছু ভিক্ষা দিলে, সেই ভক্ত যত দরিদ্রই হন না কেন, যত নিম্নশ্রেণীর মানুষই হন না কেন, সমস্ত দান গ্রহণ করতে হবে, তাই বুদ্ধদেব নিজে খাবার খেলেন। এর পরেই বুদ্ধদেব মারণ আন্ত্রিক রোগে আক্রান্ত হলেন ও তরাইয়ের পূর্বপারে কুশীনগরে চলে গেলেন ।
আনন্দকে বললেন, “ঐ দুই বলাবৃক্ষের মাঝে যে জায়গাটি দেখছ, ঐখানে ঝাঁট দিয়ে, জল দিয়ে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে আমার আসন বিছাও। আজ মধ্যরাত্রে আমার মৃত্যু হবে।
“যাও! মানুষকে জানাও যে আমার মৃত্যুক্ষণ আসন্ন। এখানে যে মল্লরা থাকেন, তাঁরা আমাকে না দেখতে পেলে খুব দুঃখ পাবেন।
শিষ্যদের সাবধান করলেন তারা যেন চুণ্ডকে তাঁর মৃত্যুর নিমিত্ত দোষারোপ না করে, বরং বললেন চুণ্ড ছিলে বলেই না তাঁর নির্বাণের দিন আরো এগিয়ে এল, চুণ্ডকে বরং ধন্যবাদ দিতে হয়।
মল্লরা চোখের জলে বিদায় দিতে এলে বললেন, “দুঃখ কর না! এ সময় আনন্দ করার সময়। দুঃখের কি ক্রোধের কোন কারণ নেই এখন। যুগ যুগান্ত ধরে যার সন্ধান করেছি, তাকে এখন অর্জন করব; চেতনার কৃশ পরিসর থেকে মুক্ত হয়ে চললাম, ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, সব কিছু পেছনে ফেলে রেখে চিরশান্তিতে যেখানে না আছে জন্ম, না আছে মৃত্যু।
“সেখানে অনন্তকালে শোক হতে মুক্তি! বল, বল, কেন আমি দুঃখ করব?”
“আমি শরীর ছাড়তে চেয়েছিলাম ঐ শীর্ষের চূড়ায়, কিন্তু আমার বিধির বিধান পূর্ণ করতে অদ্যাবধি ইহজগতে মানুষের সঙ্গে রয়েছি: বিষধর সর্পের সঙ্গে সহবাসের মতন আমার এই ভঙ্গুর, অসুস্থ শরীর আজ অবধি বয়ে চলেছি, কিন্তু এখন আমি পরম-শান্তির ধামে চললাম, সমস্ত দুঃখের বারিধারা এবার স্তব্ধ হবে।
“আর কখনো দেহধারণ করব না, ভবিষ্যতের সমস্ত শোক এই এখন চিরকালের মতন শেষ হয়ে যাবে। আর কখনো আশঙ্কায় ভীত হয়ো না।
অসুস্থ মানুষ ওষুধের রোগ সারানোর ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে, তার বৈদ্যকে না দেখলেও চলে।
আমি যা বলি তা যদি কেউ না পালন করে তবে আমাকে দেখা তার বৃথা, ওতে কোন লাভ নেই; আবার যে বহু দূরে থেকেও সৎপথে চলে, সে সদাসর্বদা আমার কাছেই থাকে।
“হৃদয়ের যত্ন নিও — সেখানে অশান্তিকে কোন জায়গা দিও না। মন দিয়ে ভাল কাজ করে যেও। বায়ু যেমন ক্রমাগত প্রদীপের শিখাকে উত্যক্ত করে, জন্ম থেকে মানুষেরও সেই এক অবস্থা — দুঃখ তাকে তাড়িয়ে বেড়ায়, এক মুহুর্তের বিরাম নেই।
শেষ মুহুর্তে পরমজন সুভদ্র নামে এক ব্যতিক্রমী সাধুকে দীক্ষা দিয়েছিলেন। তাঁকে দেখিয়েছিলেন যে এই পৃথিবী কার্যকারণ সম্ভূত, দেখিয়েছিলেন যে কার্যের নিবৃত্তিতে সব শেষ, তাঁকে অষ্টাঙ্গমার্গের শিক্ষা দিয়েছিলেন, তাঁকে সংঘে গ্রহণ করেছিলেন, এই বলে যে, “এ আমার শেষ শিষ্য যে নির্বাণ লাভ করল, এর যথাসম্ভব যত্ন নিও।
পরমজন গাছের তলায় উপবিষ্ট হয়ে শেষ নির্দেশ দিলেন, কারণ আনন্দ চাইছিলেন যে প্রভু যেন তাঁর কোলে মাথা রাখেন, মৃত্যুর এই ক্ষণে তিনি যেন তাঁর গুরুদেবের যন্ত্রণা লাঘব করতে পারেন।
বুদ্ধদেব বললেন, “শরীরের যত্ন নিও, সময়মত খাওয়া দাওয়া কোর; সালিশী বা মধ্যস্থতা কি দালালী করতে হবে এমন কোন কাজ কর না, নেশার ঘোরে কি মাদকতা করে অলৌকিকত্ব কি চমৎকারিত্ব দেখিও না, সমস্ত রকম কুটিলতাকে, ও কুটিল মনোভাব পরিহার কর; সদ্ধর্ম পালন কর; সর্বপ্রাণীর প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ো, দয়া কর, করুণা কর, যেটুকু জীবনে পাবে তাতে সন্তুষ্ট হয়ে সংযমী জীবন যাপন কর; গ্রহণ কর, কিন্তু অহেতুক জমিয়ে রেখো না; সংক্ষেপে, এইটুকুই আমার বিধান।
“শুভ-চিন্তাকে শ্রদ্ধা কর, যারা ভাল কাজ করে, মানুষের প্রতি দয়ার্দ্র কাজ করে তারাই আমার সবচেয়ে প্রিয়;
“শরতের বৃষ্টি শেষে, যখন পরিষ্কার আকাশ, মেঘ নেই, সূর্যদেব যেমন স্বর্গারোহণ করতঃ সর্বত্র তাঁর কিরণমহিমা বিস্তার করেন, তেমনি শুভ-চিন্তা অন্য সমস্ত গুণের উর্দ্ধে বিচরণ করে; প্রভাতের শুক্রগ্রহের ন্যায় সে উজ্জ্বল।
“প্রভাতে জাগ্রত মানুষ তার হৃদয়ে যে অন্ধকার পথ, তাকে সতত পরিহার করে।
“যাঁরা ক্ষমতাবান, তাঁদের প্রতি উষ্মা, ক্রোধ, কুকথাকে প্রশ্রয় দিও না। ক্রোধ ও ঘৃণা সদ্ধর্মকে ধ্বংস করে; শরীরের আভিজাত্য ও সৌন্দর্যকেও সে নষ্ট করে দেয়।
“নকুল যেমন সাপের বিষে প্রভাবিত হয় না, তেমনি যে সাধু দয়ার্দ্র চিত্তে বিচরণ করেন, সংসারের ক্রোধ আর ঘৃণার পরিবেশে থেকেও তাঁর চিত্ত বিকৃত হয় না।
“‘অল্প-বাসনা’ হতে আমরা প্রকৃত মুক্তির পথ দেখি। সত্যিকারের মুক্তি চাই বলে ‘যথেষ্ট জেনেছি’ এই বোধে সন্তুষ্ট থাকা চাই। ধনী কি দরিদ্র, যাঁরা সন্তুষ্ট, তাঁরাই সতত বিশ্রাম পান।
“চাহিদায় অতৃপ্ত হয়ো না, হলে জীবনের দীর্ঘ রাত্রিতে শুধুই দুঃখ জমতে থাকবে। যত বেশী নির্ভরশীলতা, তত বেশী বন্ধন; এই জ্ঞান না হলে মন দরিদ্র ও কপট হয়।
“বার বার বেচারা ভীত মানুষ মৃত্যুর গ্রাসে পড়ে, অলৌকিকভাবে তাদের স্বপ্ন বদলে যায়, তারা আবার ফিরে আসে সেই অজ্ঞান শিশুর নতুন শরীরে: গাছের মতন, — বাহুডোর, ভার, ক্ষীণতনু।
“সাধারণ মানুষ যেন হতভাগ্যের দল, না আছে তাদের বোধবুদ্ধি, না জানে উপায়, জাঁতাকলের নিষ্পেষণে পড়ে, অনাদিকাল ধরে চক্রাকারে আবর্তিত হয়ে চলেছে। চমরী গাই যেমন তার লেজে বাঁধা, এরাও তেমন তাদের কামনা-বাসনার জালে আবদ্ধ, দেহসম্ভোগে অন্ধ, বুদ্ধের খোঁজ আর রাখে না, সদ্ধর্মের, যাতে যন্ত্রণা হতে মুক্তি, তারও খবর রাখে না।
“এসব শুনলে হয়ত, কিন্তু মন দিয়ে মানলে না, তাতে বক্তার কোন দোষ নেই।
মাঝরাত হয়ে এল, গুরুভাইরা শান্ত দুঃখী মনে উপবিষ্ট, দেখে বুদ্ধদেব বললেন, “কে জানে হয়ত গুরুর প্রতি শ্রদ্ধাবশত তোমরা সকলে চুপ করে আছ: এস সকলে বন্ধুর মতন করে কথা বলি।”
অনুরুদ্ধ এগিয়ে এসে বললেন, “প্রভু, জন্ম মৃত্যুর সমুদ্র পেরিয়ে কামনা বাসনা রহিত, কিছু চাইবার নেই, আমরা শুধু জানি আমরা কতটা ভালোবাসি, কতটা দুঃখ পাই, তাই শুধাই বুদ্ধদেব কেন এত শীঘ্র চলে যাবেন?”
পিঙ্গিয়া বললেন, “ও আমারও হৃদয়ের কথা বলেছে।”
মানবের শ্রদ্ধেয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বললেন, “কি মনে হয় ভিক্ষুগণ? কোনটা বেশী? এই যে কেঁদে কেঁদে চোখের জলের বন্যা বইয়ে দিলে, বারংবার নতুন করে জন্ম, নতুন করে মৃত্যুর পানে ছুটে যাওয়া,একবার মিলন, তারপর যা চাই না, কাঙ্খিত জনের থেকে বিচ্ছেদ, এই বন্যার জল বেশী, না কি চার মহাসাগরের মিলিত তাবৎ জলরাশির পরিমাণ বেশী?
“বহু দিন ধরে তোমরা মাতার মৃত্যু সয়েছ, বহু দিন ধরে তোমরা পিতার মৃত্যু সয়েছ, বহু দিন ধরে সন্তানের মৃত্যু, কন্যার মৃত্যু, ভ্রাতা-ভগিনীর মৃত্যু, জিনিসপত্র হারিয়ে গেছে, ব্যধির যন্ত্রণা সয়েছ।
“কারো কারো চোখে সামান্য একটু ধুলো পড়েছে, তাদের সত্যদর্শণ হবে।
“সমুদ্রে নাবিক যখন যায়, সে একটা পাখি ছেড়ে দেয় আকাশে, সে পাখি যদি ডাঙা খুঁজে না পায় সে নাবিকের কাছে ফেরত আসে। তোমরাও তেমন, আমার কাছে ফেরত এসেছ।
“মা যেমন নিজের কথা ভাবেন না, একমাত্র সন্তানের জন্য তাঁর সকল ভালোবাসা আগলে রাখেন, তেমন করে, তোমাদের অনুকম্পা, তোমাদের ভালোবাসা যেন সারা বিশ্বের জন্যে ছড়িয়ে পড়ে।
“এমনকি ডাকাতদেরও, তাদেরও প্রেমের তরঙ্গ বইয়ে দাও জগতজুড়ে; সর্বক্ষণ ঈশ্বরীয় প্রেম করুণাধারায় ধুইয়ে দাও চরাচর, পরমানন্দে, কোন ভীতি যেন না থাকে, কারো প্রতি কোন শত্রুভাব যেন না থাকে। হ্যাঁ মোর শিষ্যগণ, এইভাবেই তোমরা তোমাদের পরম্পরাকে তৈরী কর।
“এতদূর এসে, নির্বাণলাভ করে, তোমরা কি অন্যদেরকে তীরে পৌঁছতে সাহায্য করবে না?”
আনন্দ উঠে বিষাদের গান ধরলেন,
“ পাঁচ আর কুড়ি বছর ধরে
আমি মহৎজনের সেবা করে গেছি, প্রেমভাবে তাঁর সেবা করেছি,
ছায়ার মতন তাঁর সঙ্গে ঘুরেছি।
বুদ্ধদেব যখন হাঁটতেন, তাঁর পায়ে পায়ে আমিও হেঁটেছি,
যখন ধর্মের বাণী শেখানো হত,
আমার মধ্যে জ্ঞান সঞ্চারিত হত, বুঝতাম।
হায়, আজ তিনি চলে যাবেন।
আমি পড়ে রইলাম কত কাজ বাকী,
আমি এক শিক্ষানবিশ,
এখনো যে বড় হলেম না,
আমার করুণার ফুল যে ফুটলো না,
আর আমার প্রভু আমার
হৃদয় বিদীর্ণ করে চললেন,
সেই মহাত্মা, জাগ্রতজন,
বোধি ও করুণা যাঁর পূর্ণ,
মানবের সেই অনুপম গুরু,
তিনি ভোরের শুকতারা,
তিনি প্রেমের পারাবত,
মৃগশিশু,
তিনি দুগ্ধবারিধারা,
অতীন্দ্রিয় করুণাময়,
শ্বেতরথে, বিরাট শিশু, পদ্ম-রাজ,
আমাদের মনের ঠাকুর,
চললেন, তিনি চললেন,
আমাদের শূন্যতার অদ্ভুত উজ্জ্বল আঁধারে ফেলে
তিনি চললেন!
শালবনের চারপাশে নবীন সাধুগণ ও সাধারণ গৃহীরা, তাঁরা উপলব্ধি করছেন এই মানুষটি যা শিখিয়ে গেছেন সে শুধু সত্য নয়, এতেই তাঁদের মুক্তির সম্ভাবনা, কারণ জীবনে এই প্রথমবার তাঁরা উপলব্ধি করলেন তাঁর বাণী, তাঁর আবিষ্কারের আলোয় উদ্ভাসিত, সেই সত্য, যাতে দাসত্ব শৃঙ্খল ছিন্ন করে মানুষ স্বাধীন হতে পারে, জাতপাতের বন্ধন ছিন্ন করে সবাই এক হয়ে মিলতে পারে। কিন্তু এখন, এই নশ্বর দেহের আসন্ন মৃত্যুতে তাঁরাও কম্পিত, যেন প্রজ্ঞাবান মেষগণ মৃত্যুরূপী অজ্ঞ সিংহের আগমনী বার্তা পেয়ে সন্ত্রস্ত।
আনন্দ ও সমবেত ভক্তমণ্ডলীর মন শান্ত করার নিমিত্ত বুদ্ধদেব বললেন, “আদিতে সকল বস্তু পরস্পরে আবদ্ধ ছিল, শেষে তারা আবার ছিন্ন হয়ে গেল; নানান রকমের অবস্থার মিলনে কার্য কারণ উৎপন্ন হয়, প্রকৃতিতে এক নিয়ম বলে কিছু তো নেই। কিন্তু যখন পারস্পরিক উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে, যখন তাদের প্রশ্নের উত্তর মিলবে, তখন এই জগৎ জুড়ে সৃষ্টির যে তাণ্ডব লীলা চলেছে, তার কি হবে বল তো? সেদিন ঈশ্বর আর মানুষে এক রকম ভাবে পরিত্রাণ পাবে! তাই হোক!
হে মোর ভক্তগণ, যারা সদ্ধর্ম সম্বন্ধে অবহিত আছো, মনে রেখো! একদিন সব শেষ হবে, দুঃখে বিগলিত হয়ো না।
“নিষ্ঠাভরে কাজ করে যেও; লক্ষ্য স্থির কোর সেই গৃহে পৌঁছতে যেখানে বিচ্ছেদের প্রবেশ নিষিদ্ধ; আমি জ্ঞানের প্রদীপ প্রজ্জোলিত করে গেলাম, একমাত্র এরই আলো যে বিষাদ জগতকে ছেয়ে আছে, তাকে দূর করতে সক্ষম। এ পৃথিবী তো চিরদিনের মত
ঠিক হবার নয়। তাই আনন্দ কর। ভাব, তোমাদের একটি বন্ধু আছে, যে ভারি অসুস্থ, তার আজকে রোগমুক্তি ঘটল, সে যন্ত্রণা থেকে উদ্ধার পেল। আমি যে এই যন্ত্রণাময় অবয়বটিকে ফেলে দিলাম, আমি যে ক্রমাগত জন্ম আর মৃত্যুর সমুদ্রতরঙ্গকে রুখে দিলাম, যন্ত্রণা থেকে চিরকালের জন্যে মুক্ত করে দিলাম। তাই আনন্দ কর!
“সাবধানে থেকো! স্খলিত হয়ো না, যা আছে, তা শূন্যতায় ফিরে যাবেই যাবে!
“এবার আমি চললাম
“আমার কথা ফুরোল, এই আমার শেষ শিক্ষা।”
প্রথম তূরীয় ধ্যানের সমাধিতে প্রবেশ করে বুদ্ধদেব পরপর ন’টি ধ্যানের স্তর অতিক্রম করলেন; তারপর আবার ফিরে এলেন বিপরীতমুখে প্রথম ধ্যানে; তারপর প্রথম ধ্যান থেকে নিজেকে উত্তোলিত করে চতুর্থ ধ্যানে বসলেন, না-আনন্দ না-দুঃখের ধ্যানে, যা পরমপবিত্র আদি অকৃত্রিম তন্মাত্রিক মানসের রূপ। সমাধির তূরীয় রূপ ত্যাগ করে, তাঁর আত্মা আর কোথাও না থেমে পরিনির্বাণে পৌঁছলেন, মৃত্যুর পরে যখন সমস্ত রূপ অবলুপ্ত হয়ে গেল।
চাঁদের আলো ঝাপসা হয়ে এলো, তরঙ্গিনী রোরুদ্যমানা হলেন, মানসের সমীরণে বৃক্ষরাজি হলেন নতমুখ।
মহাগজ দন্তহীন হলে যেরূপ বোধ হয়, মহাষণ্ডের শৃঙ্গবিচ্ছেদ হলে যে অবস্থা হয়, স্বর্গপুরে চন্দ্র-সূর্য-বিলোপ পেলে যে অবস্থা, ঝঞ্ঝাবাতে আহত পঙ্কজের ন্যায়, বুদ্ধদেবের প্রয়াণে পৃথিবী বিলাপ করলেন।
নির্বাণেই একমাত্র আনন্দ, সে চিরকালের মতন অব্যাহতি দেয়; কারাগার যে কারাগার থেকে উদ্ধার পাবার নিমিত্ত তৈরী হয়েছে।
চঞ্চলতার রত্নখচিত মহাদণ্ড চাঁদের পাহাড়কে উল্টে দিতে সক্ষম, কেবল তথাগতের রত্ন-আবরণ, মনের লৌহ-আবরণ তাকে জয় করতে পারে। সাধুর, বীরের, সর্বোত্তম পুরস্কার দিনশেষের মহানিদ্রার প্রশান্তি।
নিজে থেকে অগুন্তি জন্ম মৃত্যুর পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যাতে তিনি মানবজাতিকে সর্বপ্রাণকে মুক্তি দিতে পারেন, নির্বাণে প্রবেশ করতে না চেয়ে, শুধু দুঃখভোগ আর যাতনা হতে মুক্তির পথ দেখানোর শিক্ষার নিমিত্ত জগতসংসারে নিজেকে যিনি অনায়াসে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারেন, তিনিই বুদ্ধদেব, যিনি একাধারে সব হয়েছেন, সকলে হয়েছেন, অমিতাভ (অরিমিদাইয়া), যিনি জগতের আলো, তথাগত, অনাগত বীর মৈত্রেয়, জগতের শীর্ষদেশে যিনি পথ চলেছেন, যিনি বৃক্ষতলে বসেছেন, যিনি সদসৎ, যিনি অমিত শক্তিধর, আবার তীব্রভাবে যিনি মানুষ, যিনি পরমকারুণিক।
ভগবান বুদ্ধদেবের মহতী সদ্ধর্ম যেন জগতের সকলের শ্রদ্ধা পায়।
পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কিত নীতিঃ এই লেখাটি ছাপা, ডিজিটাল, দৃশ্য, শ্রাব্য, বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিলিপিকরণ বা অন্যত্র প্রকাশের জন্য গুরুচণ্ডা৯র অনুমতি বাধ্যতামূলক। লেখক চাইলে অন্যত্র প্রকাশ করতে পারেন, সেক্ষেত্রে গুরুচণ্ডা৯র উল্লেখ প্রত্যাশিত।
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
 TB | 118.171.131.186 (*) | ২৫ মে ২০১৬ ০১:২১54730
TB | 118.171.131.186 (*) | ২৫ মে ২০১৬ ০১:২১54730- অন্নচিন্তা চমত্কারা। আমার জন্য এ অতি উত্তম হইয়াছে।
কেবল দুচাট্টি কোশ্নো ছিল। এসব নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছেন দেখে ভাবছি, কোশ্নোগুলো করেই ফেলি।
বিপাসনা প্র্যাকটিস ব্যাপারটা এর মধ্যে কোথায় খাপ খায়? পশ্চিমে তো এর খুবই চল।
সতিপত্তন সুত্ত (satipatthana sutta) ই বা এই বুদ্ধ সংক্রান্ত ঘটনাবলিতে কোথায় স্থান পাবে? সেটি কতটাই বা গুরুত্বপূর্ন?
 TB | 118.171.131.186 (*) | ২৫ মে ২০১৬ ০১:৩৩54731
TB | 118.171.131.186 (*) | ২৫ মে ২০১৬ ০১:৩৩54731- শিবাংশুদার এই লিংকটাও থাক। চমত্কার কিছু প্রাসঙ্গিক বক্তব্য আছে।
http://www.guruchandali.com/blog/2015/05/04/1430728738991.html?author=somashiban
 sosen | 184.64.4.97 (*) | ২৫ মে ২০১৬ ০৩:০১54732
sosen | 184.64.4.97 (*) | ২৫ মে ২০১৬ ০৩:০১54732- এটা আস্ত বই? পিডিএফ করে লিং দিয়ে রাখলে হয় না? এরম স্ক্রোল করে করে পড়া তো অসুবিধে।
 b | 125.187.34.126 (*) | ২৫ মে ২০১৬ ০৮:১৭54733
b | 125.187.34.126 (*) | ২৫ মে ২০১৬ ০৮:১৭54733- নতুন কিছু পেলাম না।
 pi | 14.139.221.129 | ১৬ মে ২০২২ ০৮:১৪507704
pi | 14.139.221.129 | ১৬ মে ২০২২ ০৮:১৪507704- এই লেখা ভর্তি এত br/> কেন? ঠিক করে দেওয়া যায়? তাহলে পড়তে সুবিধে হত।
 kk | 174.53.251.123 | ১৬ মে ২০২২ ২০:১৭507734
kk | 174.53.251.123 | ১৬ মে ২০২২ ২০:১৭507734- এই টইটা আমি আগে দেখিনি। আস্তে আস্তে সময় নিয়ে পড়ছি এখন। কিছু প্রশ্ন তো আসবেই। প্রথমেই এই কথাটা মনে আসছে যে সিদ্ধার্থের চুল 'কাঞ্চনবর্ণ' বা 'স্বর্ণাভ' কী করে হলো? ওঁর বাবা বা মায়ের বংশে কি কোনো ককেশিয়ান লিনিয়েজ ছিলো? অরিণদা এখন গুরুতে আসেন কিনা জানিনা। অন্য কেউ উত্তর জানলে, জানালেও উপকৃত হবো।
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
-
গুরুচণ্ডা৯-র গ্রাহক হোন
কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে গুরুচণ্ডা৯-র গ্রাহক হোন। গুরুচণ্ডা৯তে প্রকাশিত লেখাগুলি পেতে চাইলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যুক্ত হোন, অথবা, আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলটির গ্রাহক হোন।
- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই
- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... )
(লিখছেন... )
(লিখছেন... অরিন)
(লিখছেন... kk, রমিত চট্টোপাধ্যায়, বিপ্লব রহমান)
(লিখছেন... Aranya )
- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন
(লিখছেন... )
(লিখছেন... )
(লিখছেন... সৃষ্টিছাড়া, সমরেশ মুখার্জী)
(লিখছেন... দীপ, হে হে, দীপ)
(লিখছেন... সমরেশ মুখার্জী, Kishore Ghosal, সমরেশ মুখার্জী)
- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... )
(লিখছেন... পাপাঙ্গুল)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... jsl)
(লিখছেন... অরিন, &/, অরিন)
- কি, কেন, ইত্যাদি
- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...
- আমাদের কথা
- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...
- বুলবুলভাজা
- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...
- হরিদাস পালেরা
- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...
- টইপত্তর
- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...
- ভাটিয়া৯
- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...
- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।
গুরুচণ্ডা৯-র সম্পাদিত বিভাগের যে কোনো লেখা অথবা লেখার অংশবিশেষ অন্যত্র প্রকাশ করার আগে গুরুচণ্ডা৯-র লিখিত অনুমতি নেওয়া আবশ্যক।
অসম্পাদিত বিভাগের লেখা প্রকাশের সময় গুরুতে প্রকাশের উল্লেখ আমরা পারস্পরিক সৌজন্যের প্রকাশ হিসেবে অনুরোধ করি।
যোগাযোগ করুন, লেখা পাঠান এই ঠিকানায় : [email protected] ।
মে ১৩, ২০১৪ থেকে সাইটটি
বার পঠিত