-
বুলবুলভাজা
-
এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়।
বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচণ্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। - গুরুভার আমার গুরু গুরুতে নতুন? বন্ধুদের জানান
- সময়ানুক্রমে | সদ্য আলোচিত | মন্তব্য অনুসারে | পঠিত অনুসারে | লেখক তালিকা
-
- নতুন আলোচনা
-
বিষয়ের শিরোনাম*:বিষয়বস্তু*:
- পাতা : ২৪২২৪১২৪০২৩৯২৩৮২৩৭২৩৬২৩৫২৩৪২৩৩

সত্যবতী - প্রতিভা সরকার
বুলবুলভাজা | ইস্পেশাল : দোল | ০৯ মার্চ ২০২৩ | ২২৭৩ বার পঠিত | মন্তব্য : ২৭, লিখছেন (Ranjan Roy, Sara Man, প্রতিভা)রাস্তার ধারে ঝুপসি গাছপালাগুলো অব্দি কুয়াশার কম্বল মুড়ি দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। একটু বাতাস বইলে দেখায় বিশাল দৈত্যের মাথা নাড়ার মতো। ধোঁয়া-ওঠা বুক নিয়ে এলিয়ে পড়ে থাকা নদীর দিক থেকে কেমন একটা গোঁওওও শব্দ ভেসে আসে, যেন কেউ কাঁদে, কষ্টে গা মোচড়ায়, নিজের গলায় নিজের দশ আঙুল চেপে ধরে। তাতে গা শিরশির করলেও অষ্টমী ভালোই জানে আসল বিপদ লুকিয়ে আছে পেছন বাগে। সে বিপদ যে কখন বিদ্যুতের মতো ঘাড়ের ওপর অব্যর্থ লাফিয়ে পড়বে কেউ জানে না। সে এক আশ্চর্য হলদে আগুনের শিখা, তাকে দেখার আগেই নিজের কানেই শুনতে পাবে নিজের ঘেঁটি ভাঙার মট মট শব্দ, আর কিছু বোঝার আগেই এতো আলহাদের শরীরখানা তেনার কষে ঝুলতে থাকবে। যেন তুমি আর মানুষ নও হে, দাঁত বার করা মরা বেড়াল একটা। শিউরে উঠে অষ্টমী তার কালো ফাটা হাতখানি কোঁকড়া চুলে ঢাকা ঘাড়ের ওপর আলগোছে বুলিয়ে নেয়। রক্ষে কর সোনার বন্ন বনবিবি, মা আমার! ভয় তাকে পেড়ে ফেলে, হঠাৎ এমন কাঁপুনি দেয় যে শরীরের সমস্ত রোঁয়া খাড়া দাঁড়িয়ে ওঠে। ... ...

বেশরম - দময়ন্তী
বুলবুলভাজা | গপ্পো | ০৮ মার্চ ২০২৩ | ২৪১৪ বার পঠিত | মন্তব্য : ২৭, লিখছেন (Dolan Champa Saha, রঞ্জন , দ)তা এই বাড়ির কোনকিছুই ওর নিজস্ব মনে হয় না, হয়ও নি কোনোদিন। আর শুধু বাড়ির কেন, এই পৃথিবীতে কোথায়ও কি ওর নিজস্ব কিছু আছে আদৌ! চাকরিটা বাবার জন্য শুরু করতে হয়েছিল, বিয়ের পরেও ছাড়তে পারে নি রমেনের জন্য। দাদার জন্যই লাইব্রেরীর চাকরি করেও পূর্বাঞ্চল সাংস্কৃতিক সঙ্ঘের হয়ে গণসঙ্গীত গেয়ে নাটক করে বেড়াতে পেরেছে। সেইটুকুই ছিল ওর নিজের আনন্দে বাঁচা। বাবা মায়ের সামনে ঢাল হয়ে দাঁড়াতো দাদা। সেই দাদাটাও অমন করে চলে গিয়ে পম্পাকে একেবারে শূন্য করে দিয়ে গেল। সেই যে ওর বুকের মধ্যে একটা আস্ত মরুভূমি ঢুকে গেল, সে কেবলই জ্বালিয়ে পুড়িয়ে একটু একটু করে প্রাণরস শুষে নিয়ে ওকে এমন তব্দাধরা কাঠের পুতুল বানিয়ে দিল। ফুলশয্যার রাত থেকে রমেন হিসহিস করে বলত ‘দ্রৌপদী! দ্রৌপদী এসছে আমার ঘাড়ে!’ পম্পাকে ব্যবহার করত ঠিক বাথরুমের মত। ওই করেই দুই ছেলে হল দেড় বছরের তফাতে। ... ...

বর্ণচোরা - এস এস অরুন্ধতী
বুলবুলভাজা | গপ্পো | ০৮ মার্চ ২০২৩ | ৯৬২ বার পঠিত | মন্তব্য : ৮, লিখছেন (এস এস অরুন্ধতী, প্রতিভা, এস এস অরুন্ধতী)
মোক্ষ আর বিদুরের খুদ - শুভাশিস পাল
বুলবুলভাজা | ইস্পেশাল : দোল | ০৮ মার্চ ২০২৩ | ১১৪৩ বার পঠিত | মন্তব্য : ৪, লিখছেন (দ, প্রতিভা, dd)৫ বছরের ছেলে হারিয়ে গেছিল হালদার বাড়ির। সবে রমতা সাধু ডেরা পেয়েছি শিব মন্দিরের ধারে তখন। রাম জানে ক মুহূর্ত নাকি ক মাস। ও বাড়ির উঠোনে আমাকে তুলে নিয়ে গিয়ে হালদার বাড়ির ছ'ভাই ছেলে ধরা ভেবে বিড়াল যেভাবে ইঁদুর ঝাঁকায় সেই ভাবে ঝাঁকাতে আমার ল্যাঙট থেকে দুটো বেলফুল পড়লো ভুঁয়ে। কষ থেকে রক্ত পড়ছে দরদর করে। মনটা আলাদা করে ফেলার চেষ্টা করছি শরীর থেকে। শুনেছি ব্যথা টের পাওয়া যায়না। কখনো কামড়ে ধরছি নিজের ঠোঁট। কোন জন্মে যেন পড়েছিলাম ব্যথার গেট থিওরি। জ্বলন্ত বাম কপালে লাগালে সুপারফিসিয়াল ব্যথার চোটে দপদপানি গভীর ব্যথা ফটক দিয়ে ঢোকার সুযোগ পায়না। ... ...

কাফকীয় সকাল - শুভব্রত আচার্য্য
বুলবুলভাজা | ইস্পেশাল : দোল | ০৮ মার্চ ২০২৩ | ৪৭৭ বার পঠিতঘুম থেকে উঠে ঋজু বুঝল মাথাটা অসহ্য ধরেছে। কিন্তু সে এই সক্কাল সক্কাল বুঝে উঠতে পারল না, চশমার পাওয়ারটা হঠাৎ বেড়ে গেলো নাকি বইয়ের লেখা গুলো ক্রমশ ছোট হয়ে যাচ্ছে। দিন দিন কাগজের দাম যে হারে বাড়ছে তাতে কোন কিছুই অসম্ভব নয়, নিজের মনেই বলে উঠলো সে। মুখ ধুয়ে, বিষ্ণুদার দোকানের চা টাই এর মহৌষধ, তাই হোস্টেলের নীচে নামটাই এখন তার একমাত্র ভরসা। অভ্যেস মতো চা অর্ডার দিয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে তার মনে হল, ভেতরের যা সব পুড়ছে তারা এতক্ষণে একটা বেরোবার পথ পেয়ে নিস্তার পেল। ... ...

স্যাটেলাইট ট্রান্সফার - মোহাম্মদ কাজী মামুন
বুলবুলভাজা | ইস্পেশাল : দোল | ০৭ মার্চ ২০২৩ | ১১৯০ বার পঠিত | মন্তব্য : ১৪, লিখছেন (Md Rakibul Islam, তুষার কান্তি মাহাতো, Debiprasad Batabyal )চেম্বারটির সাথেই একটা জানালা ছিল, সে জানালাটা ধরে দাঁড়িয়ে ছিল মোরসালিন। শম্পা চলে যাওয়ার পর ফাইলগুলো নিয়ে বসেছিল, এর মধ্যে তো একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল, একটি বিশাল বিজনেস প্লান, কোম্পানির এই শাখা অফিসটার চেহারা একাই বদলে দেয়ার ক্ষমতা রাখে। কিন্তু কিছুদূর যেয়ে মাথাটা গুলিয়ে গিয়েছিল! এত দিন ধরে মেহনত করেছে যার জন্য, যার পুরো রূপরেখাটা তার দেয়া, সেই কাঠামোটাই যেন খুব অচেনা লেগেছিল, আর মাথাটা ঘুরতে শুরু করেছিল। জানালাটার বাইরে তখন চলচ্চিত্রের রিলের মত ছুটে চলেছিল মানুষ, যানবাহন। এমনকি একটা নেড়ি কুকুরকেও রুদ্ধশ্বাসে দৌড়ুতে দেখা গেল, কি এক গুরুত্বপূর্ণ মিশনে রয়েছে যেন সে, কিসের যেন এক তাড়া! এমনই এক তীব্র চলার স্রোত জানালার নীচের রাস্তাটিতে যে মনে হয়, জড় দোকানপাট ও বিপনিবিতানগুলোরও চাকা গজিয়েছে! ... ...

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ - অনিন্দিতা গোস্বামী
বুলবুলভাজা | ইস্পেশাল : দোল | ০৭ মার্চ ২০২৩ | ৮২৩ বার পঠিত | মন্তব্য : ২, লিখছেন (মোহাম্মদ কাজী মামুন, বিপ্লব রহমান)তবে এই সহজ ব্যাপারটাও কিন্তু সহজে রপ্ত হয়নি নিশিগন্ধার। সে এরমধ্যেই অনেক রঙ ঢঙ দেখিয়ে ফেলেছে। সেটা কিরকম? সিগারেটের প্যাকেটের গায়ে লেখা বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণে যেমন লেখা থাকে স্মোকিং ইঞ্জুরিয়াস টু হেলথ তা সত্ত্বেও লোকে ফকফক করে সিগারেট খায় তেমনি রগচটা সুদীপের সঙ্গে সে একটু বেশি মাখামাখি করতে গেছে। তর্ক ঝগড়াও করতে গেছে। ভেবেছে এরপর ভাব হলে খুব মজা হবে। তা তো হয়ই নি। উলটে শঙ্কর মাছের লেজ উঠে এসেছে দীঘার সমুদ্র থেকে। ... ...
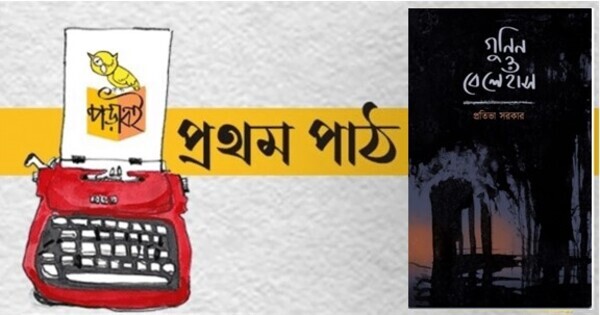
তাদের গল্প, যাদের দেখেও দেখি না, শুনেও শুনিনা - সৌমী আচার্য্য
বুলবুলভাজা | পড়াবই : প্রথম পাঠ | ০৫ মার্চ ২০২৩ | ১৩৭৪ বার পঠিত | মন্তব্য : ৬, লিখছেন (সুস্মিতা দত্ত, স্বাতী রায়, দ)কথা বাড়াতে ইচ্ছে করবে না বলেই হাঁটব। আমার পাশেপাশে যারা ভীড় জমাবে তাদের গা থেকে উঠে আসা ধোঁয়া গন্ধে ভয় পাব না। না জেনে না চিনে অযথা ভয়ে একটা অভিশপ্ত জীবন আঁকব না, এটুকু অন্তত আমার উত্তরণ ঘটবে আমি নিশ্চিত। গুনিনের বুকের ভিতর কোন ঝড় গেঁথে তুলেছেন লেখিকা সেকথা ভাবতে ভাবতে বরং অন্ধকারের গায়ে আঙুল রাখব। কেউ হয়ত গল্প শোনাবে তাদের গুনিন হবার কাহিনী। ভুলভ্রান্তিতে ভরা ভয়ংকর দানবীয় ইতিবৃত্ত। লেখিকাও যে 'গুনিন' গল্পে বুক মুচড়ে ওঠা শব্দটুকু লিখেছেন, ভাবতে থাকব... ... ...
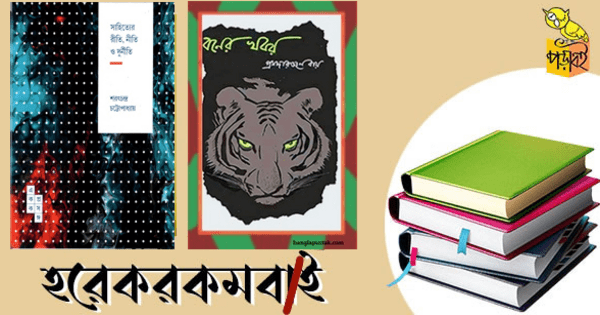
হরেকরকমবই— ১৩ - দিব্যেন্দু সিংহরায়
বুলবুলভাজা | পড়াবই : হরেকরকমবই | ০৫ মার্চ ২০২৩ | ৮২৯ বার পঠিত | মন্তব্য : ১, লিখছেন (kk)প্রমদারঞ্জন রায়ের বনের খবর ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাহিত্যের রীতি, নীতি ও দুর্নীতি - দুটি বই নিয়ে আলোচনা করলেন দিব্যেন্দু সিংহ রায়। ... ...
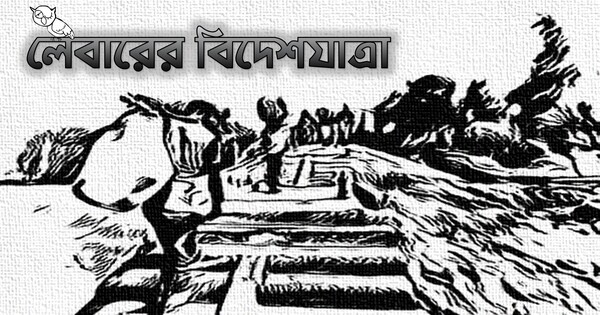
লেবারের বিদেশ যাত্রা ১৪ - মঞ্জীরা সাহা
বুলবুলভাজা | ধারাবাহিক : সমাজ | ০৪ মার্চ ২০২৩ | ১০৯৫ বার পঠিত | মন্তব্য : ১, লিখছেন (মোহাম্মদ কাজী মামুন)জল নয়। জল নয়। খটখটে রোদে চকচক করে ওঠা বালি ওখানে। সেই গল্পের মত। ওরকম জলের মত দেখতে লাগে। কাছে গিয়ে দেখা যায় বালি। বলে মরীচিকা। ঠা-ঠা-পোড়া রোদে গা-হাত-পা-সারা শরীর যেন জ্বলে জ্বলে উঠছে। এই কোথায় গেল! করকর করা চোখ দুটো গুনছে এবার। উনষাট, ষাট, একষট্টি, বাষট্টি… না একটা নেই তো। চারিদিকে যতদূর বালির ঢেউয়ের দিকে চোখ যায়, খোঁজার চেষ্টা করছে। তারপর ঝাপসা। আটষট্টি, ঊনসত্তর… না মিলছে না। কোনও একটা নাম ধরে চ্যাঁচাচ্ছে। আলম ইকবাল বা ইমরান…। ডাকছে। বারবার। মুখের ভেতর শুকনো জিভটা নড়ে নড়ে উঠছে। শুকনো গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোতে চাইছে না। বা-আ-বু…ল আ-বু…ল। না, সাড়া নেই। ... ...

পূর্ব ইউরোপের ডায়েরি – বসনিয়া হার্জেগোভিনা এবং রেপুবলিকা স্রাপসকা ১ - হীরেন সিংহরায়
বুলবুলভাজা | ধারাবাহিক : ইতিহাস | ০৪ মার্চ ২০২৩ | ১৪০০ বার পঠিত | মন্তব্য : ৩, লিখছেন (মোহাম্মদ কাজী মামুন, Tapan Kumar SenGupta, Kishore Ghosal)ক্রোয়েশিয়ান চৌকির পুলিস কিঞ্চিৎ কৌতূহলী। আমার চেহারার সঙ্গে আমার পাসপোর্টের রঙ, গাড়ির নম্বর প্লেট এবং পার্শ্ববর্তিনীর মুখ কোনটাই মেলে না, প্রায় কখনোই। চার দশক কেটে গেছে, পুলিশের বিস্ময় আমাকে আর বিস্মিত করে না। এখন কেবল পরবর্তী সংলাপের অপেক্ষা। পরিচ্ছন্ন ইংরেজিতে জানতে চাইলেন ঠিক কোথায় যাচ্ছি—মস্তার? বললাম, মস্তার যাবো, তবে মেজুগরিয়ে হয়ে। রোদিকাকে দেখিয়ে বললাম ইনি যে অত্যন্ত ধর্মপ্রাণা মহিলা, একবার মা মেরির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান! ... ...

সীমানা - ২৪ - শেখরনাথ মুখোপাধ্যায়
বুলবুলভাজা | ধারাবাহিক : উপন্যাস | ০৪ মার্চ ২০২৩ | ২১৯৯ বার পঠিত | মন্তব্য : ১, লিখছেন (রঞ্জন রায়)পত্রিকার নাম ধূমকেতু, তার সম্পাদককে বলা হল সারথি। উনিশশো বাইশের এগারই আগস্ট বেরল প্রথম সংখ্যা ধূমকেতু, রবীন্দ্রনাথের একটি বাণী তার শিরোভূষণ। এর এক বছর আগে, উনিশশো একুশের সেপ্টেম্বরে, জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে এক বহুল প্রচারিত আলোচনায় রবীন্দ্রনাথকে অসহযোগ আন্দোলন, বিদেশী বস্ত্র বয়কট এবং চরকাস্ত্র প্রয়োগে স্বরাজের ভাবনায় নিজের মতে আনতে ব্যর্থ হয়েছিলেন গান্ধী। এক বছর পর নজরুলের এই প্রয়াসকে প্রাণ-ভরে আশীর্বাদ জানালেন কবি! ... ...
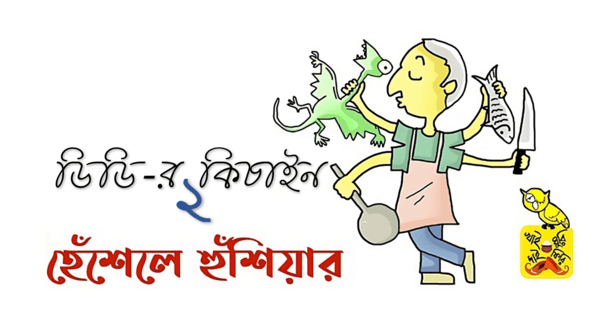
ডিডি-র কিচাইন - সীজন টু - ১ - ডিডি
বুলবুলভাজা | খ্যাঁটন : হেঁশেলে হুঁশিয়ার | ০২ মার্চ ২০২৩ | ১৬১৬ বার পঠিত | মন্তব্য : ১৫, লিখছেন (dc, PM, aranya)কোন সবজেক্টে ব্যাবাক মানুষে, মানে ভারত তথা বাংলা তথা গুরুচন্ডালীর সব্বাই, যাকে বলে একেবারে হুলিয়ে পন্ডিত? মানে যাকে বলে প্রাজ্ঞ? না, না, ফুটবল নয়, পোলিটিক্স নয়, সাহিত্য বা ক্যালকুলাসও নয়। আসলে সবাই যে ব্যাপারে মতামতে ভর্পুর এবং অভিজ্ঞতায় উপছে পড়েন সেটা হচ্ছে বিরিয়ানি। একবার হাটে হাঁড়ি ভেঙেই দেখুন না, ঘটি বাঙাল, বাসী, প্রবাসী বা অ্যান্টিবাসী, তরুন বা বুড়োটে, সব সব রকমের জেন্ডার - মানে সকলেই তাদের অফুরন্ত অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান ভান্ডার নিয়ে হাজির হবেন। তক্কো জুরে দিবেন, কোনটি খাঁটি আর কোনটি বর্ণ সংকর দুষ্ট, কে অথেন্টিক, কে নকল নবীস। শেষ কথা কে কবে? ... ...

পাকশালার গুরুচণ্ডালি (৬২) - শারদা মণ্ডল
বুলবুলভাজা | খ্যাঁটন : হেঁশেলে হুঁশিয়ার | ০২ মার্চ ২০২৩ | ১০৮১ বার পঠিত | মন্তব্য : ২, লিখছেন (kk, Sara Man)— চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগে শহুরে সংস্কৃতি গ্রামে খুব একটা ঢোকেনি। টিভিও খুব কম ঘরে ছিল। তাই ব্যাপারটা লেখাপড়ার জন্য নয়। লেখাপড়ার চর্চা ওসব জায়গায় খুব ভালো ভাবেই ছিল। তারিণীপ্রসাদ আর তাঁর বয়স্যরা মিলে স্বাধীনতার পরে তৈরি করেছিলেন ঐ এলাকার ছেলেদের জন্য প্রথম হাইস্কুল। আর মেয়েদের ইস্কুল শুরু হয়েছিল তোর ঠাকুমা বেলারানীর তত্ত্বাবধানে, তোদেরই বাড়ির দাওয়াতে। — এই তো, এবার ইস্কুলের গল্প চলে এসেছে। বল, বল পুরোটা। কিন্তু আমি তো জানতাম ইস্কুল, হাসপাতাল সব কিছু বুড়ো ঠাকুরদা তারিণী করেছেন। এর মধ্যে ঠাকুমাও ছিল! ঠাকুমা লেখাপড়া জানতো? একটু খুলে বল দেখি। ... ...

আমার স্বদেশ লুঠ হয়ে যায় প্রতিদিন প্রতিরাতে – আমাদের “হিন্দু” হয়ে ওঠা - জয়ন্ত ভট্টাচার্য
বুলবুলভাজা | আলোচনা : রাজনীতি | ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ | ২৫৮৬ বার পঠিত | মন্তব্য : ৬, লিখছেন (গোরা , Utpal Roy, soumya chakraborty)প্রসঙ্গান্তরে, প্রতিবছর আমরা ১৫-ই আগস্ট তথা স্বাধীনতা দিবসের দিনটিতে যথেষ্ট পরিমাণ বেলপাতা-ফুল-পাঁজি-বাতাসা নিয়ে স্বাধীনতার গল্প শুনি। ২০১৭ সালে দুই দিনাজপুর এবং মালদার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ভয়ঙ্কর বন্যা শুরু হয়েছিল ১৫ আগস্ট। এক হাঁটু জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে গ্রামের এক স্কুলের প্রধান শিক্ষক আমাদের জাতীয় পতাকা তুলেছিলেন, সাথে কয়েকজন বাচ্চা শিক্ষার্থী ছিল। পরের দিন সংবাদপত্রের খবর হয়েছিল এ ঘটনা। সমস্ত বঞ্চনা, অনাদর, অবহেলা, অবান্তর মৃত্যু, বুভুক্ষা, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের হাজারো ঝড়ঝাপটা সত্ত্বেও মানুষের স্মৃতিতে নির্মিত হয় স্বাধীনতা দিবসের বর্ণময় চিত্রকাব্য – এমনকি জীবনে কোন বর্ণ না থাকা সত্ত্বেও। এখানে এসে বিভিন্ন তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা – হবসবম, হানা আরেন্ট, নর্বার্ট এলিয়াস, স্পিভাক, লাকাঁ আদি সমস্ত বিশ্ব তত্ত্বসাম্রাজ্যের শাসক সম্রাটেরা – ভেঙ্গে পড়তে থাকে মানুষের শরীরী অভিজ্ঞতা বা emobodied experience-এর কাছে। অদ্ভুতভাবে অনেকেরই সেদিন মনটাও হয়তো বা একটু উড়ুক্কু থাকে। ... ...
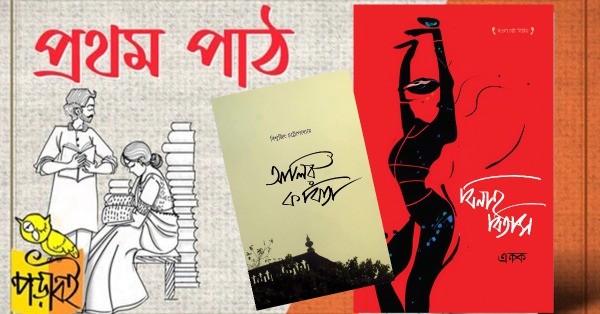
দুটো ব্যক্তিগত কবিতার বই - দীপাঞ্জন মুখোপাধ্যায়
বুলবুলভাজা | পড়াবই : প্রথম পাঠ | ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ | ১০২৬ বার পঠিত | মন্তব্য : ২, লিখছেন (মোহাম্মদ কাজী মামুন, দীপাঞ্জন মুখোপাধ্যায়)
পাকশালার গুরুচণ্ডালি (৬১) - শারদা মণ্ডল
বুলবুলভাজা | খ্যাঁটন : হেঁশেলে হুঁশিয়ার | ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ | ১০৫৬ বার পঠিত | মন্তব্য : ২, লিখছেন (মোহাম্মদ কাজী মামুন, Sara Man)বিয়ের পরে নতুন বউ, শ্বশুর বাড়িতে দুর্গাপুজো, শাশুড়ি বরণ শেখাচ্ছেন, সিঁদুর খেলা, বরের ক্যামেরায় সিঁদুর মাখা মুখের ছবি, মত্ত হয়ে ছিলাম। বাড়িসুদ্ধ সবাই মাতোয়ারা। হঠাৎ চোখে পড়লো, সবার প্রিয় বড়দি, আমার বড় ননদ ঘরে মুখ চেপে ডুকরে কাঁদছে। বিধবা বলে এই আনন্দে তার অধিকার নেই, নিজের বাড়িতেও। সেদিন বিজয়ার আর একটা নির্মম মানে বুঝলাম - সধবার স্বীকৃতি আর আনন্দের তলায় বিধবার দুঃখ। সধবার অধিকারের উলটো দিকে রয়েছে বিধবার নিঃসঙ্গতা - একরকম সামাজিক বহিষ্কার। এ চাবুক চোখে দেখা যায়না, তাই আসল চাবুকের চেয়ে অনেক কঠিন আর ধারালো, চামড়া কেটে গভীরে বসে যায়। ঐ দৃশ্য দেখার আগে বিজয়া দশমী যে কিছু মেয়ের জন্য এতটা অপমানের তা বুঝতে পারিনি। এখন দশমীর বরণে পারুল কে ডাকি। অল্প বয়সে পারুলের বর সুরাটে কাজ করতে গিয়ে এইডসে মারা যায়। তিনটি শিশু সন্তানসহ একঘরে পারুলকে শাশুড়ি আশ্রয় দেন। পারুল বলে, "হ গো বৌদি, মো কি ঘরো পূজা করিনা? শুধু সিন্দুর দিবানি, প্রদীপ, ধূ্প, মিষ্টি, জড়ো, পানো সবু দিবা"। প্রথাগত শিক্ষার নাগালের বাইরে থাকা আত্মবিশ্বাসী নারীকে বড় ভালো লাগে। ... ...
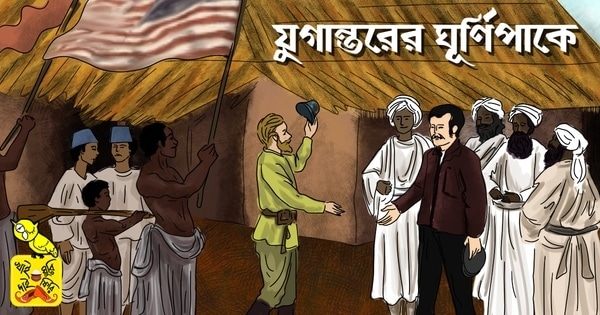
ডেভিড লিভিংস্টোনের খোঁজে-১১০ - হেনরি মর্টন স্ট্যানলে
বুলবুলভাজা | ভ্রমণ : যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে | ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ | ৮৬৩ বার পঠিততার গ্রামে আস্তানা গাড়ার পরেই আমাদের সঙ্গে দেখা করতে রুহিঙ্গা এসেছিল। অতিশয় সহৃদয় লোক, সবসময়ই হেসে ওঠার কারণ খুঁজছে; সম্ভবত মুকাম্বার চেয়ে পাঁচ - ছ বছরের বড় - যদিও তার নিজের মতে তার একশ বছর বয়স - তবে সে তার ছোট ভাইয়ের মত অত সম্মানিত নয়, আর ভাইটিকে তার নিজের লোকেরা যেমন শ্রদ্ধা-ভক্তি করে, একে তত কিছু করে না। রুহিঙ্গা অবশ্য মুকাম্বার চেয়ে দেশের সম্পর্কে বেশি জানে। আর তুখোড় স্মৃতি শক্তি! খুব বুদ্ধিদীপ্ত ভাবে তার দেশ সম্পর্কে জ্ঞান আমাদের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছিল। সর্দার হিসাবে আমাদের যথাযথ সম্মানও দেখিয়েছিল - একটা ষাঁড়, একটা ভেড়া, দুধ আর মধু উপহার দিয়েছিল - আমরাও তার থেকে যতটা সম্ভব তথ্য বের করার চেষ্টা করতে পিছপা হইনি। রুহিঙ্গার থেকে যা জেনেছিলাম তার সংক্ষিপ্তসার অনেকটা এইরকম। ... ...

HIV /AIDS Act, ২০১৭ ও কিছু কথা - Jaydip
বুলবুলভাজা | আলোচনা : স্বাস্থ্য | ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ | ৯৬০ বার পঠিত | মন্তব্য : ৪, লিখছেন (kk, ইন্দ্রাণী, Amit tor friend (RBU))বহু প্রতীক্ষার পর যখন ২০১৭ তে এসে এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তিদের মানবাধিকার রক্ষার জন্য তৈরী হওয়া এইচআইভি ও এইডস আইন ২০১৭ পাশ হয়েছে। এই আইন সারা দেশে ১০ই সেপ্টেম্বর ২০১৮ থেকে কার্যকর করা শুরু হয়ে গেছে। চলুন সংক্ষেপে জেনে নিই কি বলছে আইন... ... ...
গদ্য সাহিত্যের অনুবাদ প্রসঙ্গে আশীষ লাহিড়ীর সঙ্গে খোলামেলা আড্ডাঃ পর্ব ২ - রূপক বর্ধন রায়
বুলবুলভাজা | আলোচনা : বিবিধ | ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ | ১৩১৭ বার পঠিত | মন্তব্য : ৩, লিখছেন (শুদ্ধসত্ত্ব দাস, Mantu Lahiri, রূপক বর্ধন রায়)সে যাই হোক, তোমায় একটা আবিষ্কারের গল্প বলি শোনো। এসব কথায় কথায় উঠে আসে। সুগতবাবু রবীন্দ্রনাথকে নানান জায়গায় কোট করেছেন ওঁর বইতে, তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিকতা বা কট্টর-জাতীয়তাবাদ-বিরোধিতা ইত্যাদির উপর জোরও দিয়েছেন। তো এক জায়গায় ১৮৯৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বরে নতুন শতাব্দীর সময়টাকে ধরতে গিয়ে উনি রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতাটা কোট করছেন, 'শতাব্দীর সূর্য আজি রক্তমেঘ মাঝে অস্ত গেল'। এইটা দিয়ে উনি তখনকার পরিস্থিতিটাকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছেন, যে কেন রবীন্দ্রনাথ এটা লিখলেন। এইটারই আবার রবীন্দ্রনাথের করা একটা অনুবাদ ন্যাশনালিজম বইয়ের পরিশিষ্টে আছে। তো আমি রবীন্দ্রনাথের বাংলাটা আর ইংরেজিটা মেলাতে গিয়ে দেখলাম ইট ইজ এ রেভিলেশান। কারণ প্রথম লাইনগুলো হুবহু এক, কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু তারপর দেখি কবিতার লাইন আর মিলছে না। আবার কয়েকটা লাইনে দেখি নাহ এই কবিতা থেকেই নেওয়া, খানিক দূর যাওয়ার পর দেখি আবার মিলছে না! ইংরেজি কবিতাটা বেশ বড়, আর বাংলাটা ততটা বড় নয় কারণ ওটা সনেট- ১৪ লাইনের। বাংলাটা লেখা হয়েছিল ১৮৯৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর, আর উনি ওটার ইংরেজি করছেন ১৯১৩ কি ১৪ সালে- যদ্দূর সম্ভব; কাজেই ততদিনে তার মধ্যে কিছু পরিবর্তন এসেছে। ... ...
- পাতা : ২৪২২৪১২৪০২৩৯২৩৮২৩৭২৩৬২৩৫২৩৪২৩৩
-
গুরুচণ্ডা৯-র গ্রাহক হোন
কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে গুরুচণ্ডা৯-র গ্রাহক হোন। গুরুচণ্ডা৯তে প্রকাশিত লেখাগুলি পেতে চাইলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যুক্ত হোন, অথবা, আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলটির গ্রাহক হোন।
- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই
- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... )
(লিখছেন... অসিতবরণ বিশ্বাস , দ)
(লিখছেন... PRABIRJIT SARKAR, অমিতাভ চক্রবর্ত্তী)
(লিখছেন... অমিতাভ চক্রবর্ত্তী)
(লিখছেন... কচ্ছপ, Debasis Bhattacharya, Debasis Bhattacharya)
- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন
(লিখছেন... হীরেন সিংহরায়, হীরেন সিংহরায়, শিবাংশু)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... অসিতবরণ বিশ্বাস , দ, aranya)
(লিখছেন... দ, Nirmalya Nag)
(লিখছেন... হীরেন সিংহরায়, পাপাঙ্গুল, মোহাম্মদ কাজী মামুন)
- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... :|:, রঞ্জন , :|:)
(লিখছেন... ., Guru, Guru)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... দীপ, দীপ , ar)
(লিখছেন... কৌতূহলী, Debasis Bhattacharya, কৌতূহলী)
- কি, কেন, ইত্যাদি
- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...
- আমাদের কথা
- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...
- বুলবুলভাজা
- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...
- হরিদাস পালেরা
- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...
- টইপত্তর
- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...
- ভাটিয়া৯
- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...
- বুলবুলভাজা গুরুচন্ডা৯-র সম্পাদিত বিভাগ। এই বিভাগে প্রকাশিত লেখা অন্যত্র প্রকাশের ক্ষেত্রে গুরুচণ্ডা৯ ও লেখকের অনুমতি ও উল্লেখ প্রয়োজনীয় । টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই । ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত ।


