-
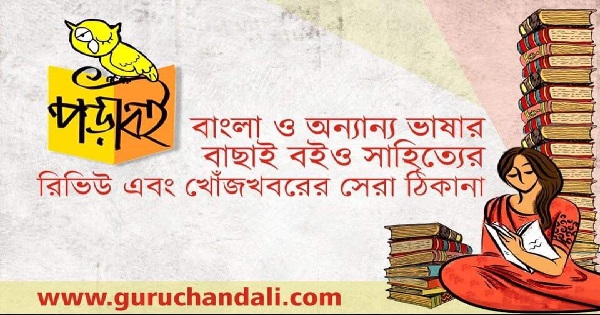 বুলবুলভাজা পড়াবই
বুলবুলভাজা পড়াবই
-
এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়।
বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচণ্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। - গুরুভার আমার গুরু গুরুতে নতুন? বন্ধুদের জানান
- সময়ানুক্রমে | সদ্য আলোচিত | মন্তব্য অনুসারে | পঠিত অনুসারে | লেখক তালিকা
-
- নতুন আলোচনা
-
বিষয়ের শিরোনাম*:বিষয়বস্তু*:
- পাতা : ১৮১৭১৬১৫১৪১৩১২১১১০৯
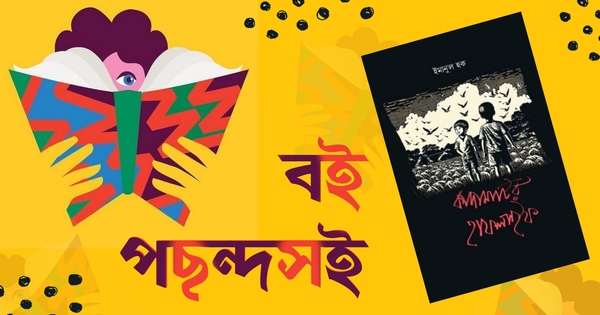
পুস্তক সমালোচনা : কাদামাটির হাফলাইফ (ইমানুল হক) - সঞ্জীব দেবলস্কর
বুলবুলভাজা | পড়াবই : বই পছন্দসই | ০৭ জুলাই ২০২৪ | ৩৮৫ বার পঠিত | মন্তব্য : ৪, লিখছেন (Prativa Sarker, দ, মোহাম্মদ কাজী মামুন)
পুস্তক সমালোচনা : স্বর্ণকুমারীর মৃত্যু ও জীবন, নয়নজোড়া কৌমুদী - প্রতিভা সরকার
বুলবুলভাজা | পড়াবই : প্রথম পাঠ | ২৩ জুন ২০২৪ | ৩৫২ বার পঠিতপুজোর লেখার তাড়া তো রয়েইছে। তাই বলে তো আর হুমড়ি খেয়ে সবসময় লেখা যায় না, তাই লেখা, পড়া, সংসারের কাজ, প্রায়ই বিরাট দেশটার অলিগলি চিনে নেবার জন্য বেরিয়ে পড়ার প্রস্তুতি, এইসবের ফাঁকে ফাঁকে খুব ভালো বই পেলে এখনও গোগ্রাসে পড়ে ফেলি। সেইরকম বইয়ের সংখ্যা দিন দিন আমার দেরাজে বর্ধমান! এবার আসানসোলে বসেই পড়ে নিলাম জয়া মিত্র-দির “স্বর্ণকুমারীর মৃত্যু ও জীবন” আর তার পরেই একেবারে অন্য স্বাদের আর একটি, অর্দ্ধেন্দুশেখর গোস্বামীর “নয়নজোড়া কৌমুদী।” ... ...
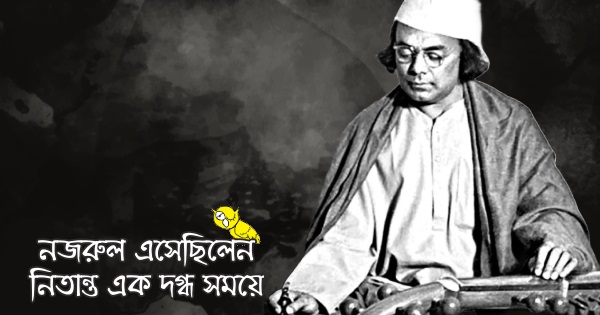
নজরুল এসেছিলেন নিতান্ত এক দগ্ধ সময়ে - সৈয়দ তৌশিফ আহমেদ
বুলবুলভাজা | পড়াবই : মনে রবে | ২৫ মে ২০২৪ | ৬৭৮ বার পঠিত | মন্তব্য : ৫, লিখছেন (বিপ্লব রহমান, বিপ্লব রহমান, Kishore Ghosal)প্রতিকূলতার মুখে দাঁড়িয়ে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবনা যেভাবে প্রত্যাঘাত করেছে, সেটাকেই নজরুল শব্দের স্বচ্ছন্দ গতিতে রূপান্তর ঘটিয়ে গেছেন বরাবর, কিছুটা একবগগা এবং ছেলেমানুষের মতই। গূঢ় দর্শন তাঁর লেখার বাঁধনহারা উচ্ছলতায় খাদ মেশায় নি কখনও, তেমনই পুনরাবৃত্তিও পিছু ছাড়েনি। নজরুল ঠিক এখানেই স্বেচ্ছাচারী অসংযমী অসচেতন, এবং তাঁর সৃষ্টির অনেকাংশই গভীর ভাবলোকে অনুত্তীর্ণ। তবে ওই ঐচ্ছিক খামতিগুলোই কি তাঁকে অনন্য করেনি? তিনি তো একাই হয়ে উঠেছেন একটা ঘরানার আদি ও অন্ত। পূর্ব ও উত্তরসূরি না থাকা এক অদ্বিতীয় ধারা। এমনই এক তেজস্ক্রিয়তা, অর্ধ জীবনকালের সূত্র মেনে যার ফুরিয়ে যাওয়াটা নির্ধারিত। সেই ফুরিয়ে যাওয়াতেও অবশ্য তাঁর মস্ত সাফল্য। ... ...
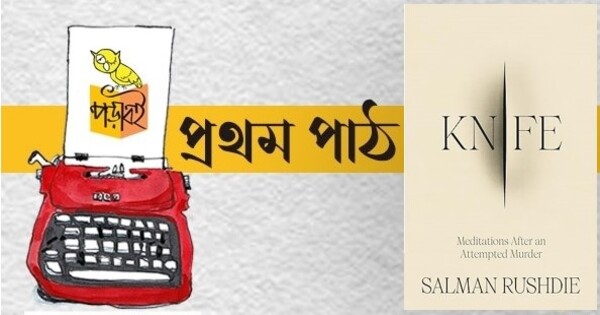
সাতাশ সেকেন্ড, মৃত্যুর মুখোমুখি - সোমনাথ গুহ
বুলবুলভাজা | পড়াবই : প্রথম পাঠ | ১২ মে ২০২৪ | ৯১২ বার পঠিত | মন্তব্য : ৯, লিখছেন (dc, PRABIRJIT SARKAR, sch)ঘৃণা, হিংসার এই বাতাবরণে একজন লেখক কী করবেন? রুশদি মিথিক্যাল গ্রিক পয়গম্বর, সংগীতকার অরফিউয়াসকে স্মরণ করছেন। তাঁর মাথা ছিন্ন করে যখন তাঁকে হেব্রাস নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল তখনও অরফিউয়াস গান থামাননি, তাঁর সংগীত দূরদূরান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই ভয়াবহতার আবহে আমাদেরও আজ গান গেয়ে যেতে হবে, জোয়ারের দিক পরিবর্তনের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। ... ...

আমার জার্মানি - জলের ধারে বসে থাকার স্মৃতি - অভিজিৎ সেন
বুলবুলভাজা | পড়াবই : বই পছন্দসই | ১২ মে ২০২৪ | ৬৬৫ বার পঠিত | মন্তব্য : ১, লিখছেন (অমিতাভ চক্রবর্ত্তী)‘আমার জার্মানি’ বইটা পড়ে শেষ করার পর খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকা ছাড়া উপায় নেই। তবে হ্যাঁ, যদি কেউ বলেন যে আমি এই বইটা এক নিঃশ্বাসে পড়ে শেষ করেছি তাহলে তাঁকে বলতেই হবে যে ক্ষমা করবেন মহোদয়, আপনার বোধহয় কোথাও ভুল হচ্ছে’, কারণ ওটা সম্ভব নয়। এ বই পড়তে হবে থেমে থেমে , রসিয়ে রসিয়ে, অনুভব করে করে, প্রত্যেকটা অনুচ্ছেদের মর্ম অনুধাবন করে। ... ...
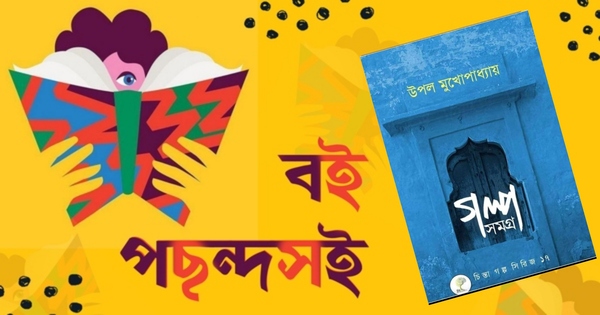
গল্পসমগ্র’ (২০২২) প্রথম খণ্ড (উপল মুখোপাধ্যায়) - পুরুষোত্তম সিংহ
বুলবুলভাজা | পড়াবই : বই পছন্দসই | ২২ এপ্রিল ২০২৪ | ৬৩৩ বার পঠিতবিজ্ঞাপনের মোহিনী মায়া, সংবাদের আলো-আঁধারি ভাষা, কুঞ্ঝটিকা, বাজার ধরার কৌশল সমস্ত মিলিয়ে যে ফাঁদ তার প্রগাঢ় ভাষ্য উপল নির্মাণ করে নেন। সেই নির্মাণে গপ্প হিসেবে উপলকে অনেক সময়ই বাস্তবের আড়ালে চলে যেতে হয়। বাস্তবকে ধরে অপ্রচ্ছন্ন বাস্তবের প্রতিমূর্তি গড়ে তোলেন। সেই অপ্রচ্ছন্ন বাস্তবের ছায়ামূর্তির মধ্যেই বাস্তবের প্রতিমা লুকিয়ে আছে। সেখানে পাঠক বাস্তবকে আবিষ্কার করবেন বা প্রত্যাখ্যান করে অধিবাস্তবের স্বরকে দেখবেন সেটা পাঠকের প্রত্যাশার উপর ছেড়ে দেন। পাঠকের ভাষ্যে তা শিল্প হতেও পারে আবার নাও হতে পারে। সেসব নিয়ে উপলের কোনো মাথা ব্যথা নেই। তিনি শিল্প বা না-শিল্প বৃত্তের ভাবনায় পাঠককে যে মাতিয়ে রাখতে পারেছেন সেটাই তাঁর সার্থকতা। হ্যাঁ তিনি রীতিমতো পরীক্ষা নিরীক্ষা করে যান। গদ্যসেতু ধরে ভাবনার তরঙ্গ বিচ্ছুরণে পাঠকের মস্তিষ্কে একাধিক বিরোধাভাসের জাল বুনে দিতে চান। সেখান থেকে পাঠক বাস্তবের সত্যে ফিরুক বা বাস্তবকে অস্বীকার করে শিল্পের সত্য বুঝে নিক। ... ...
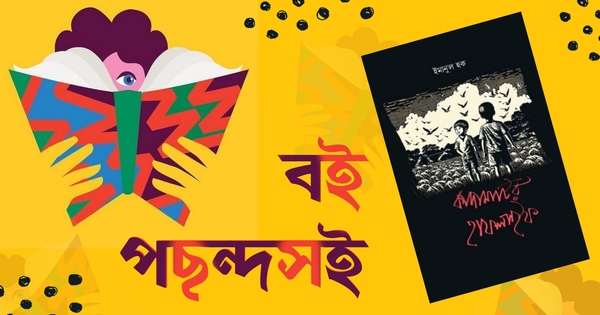
পুস্তক সমালোচনা : কাদামাটির হাফলাইফ (ইমানুল হক) - প্রদীপ দাস
বুলবুলভাজা | পড়াবই : বই পছন্দসই | ২১ এপ্রিল ২০২৪ | ৪৭২ বার পঠিত | মন্তব্য : ১, লিখছেন (দ)বইটি পড়া শেষ করে মাথায় একটা কথা ঘুরপাক খাচ্ছে এবং মনে হচ্ছে যে এই বইটি না পড়ে মরে গেলে বড্ড অন্যায় হয়ে যেতো। প্রায় প্রতিটি অধ্যায়ের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বারবার মনে হয়েছে যে এই বই আমার জীবনের ফেলে আসা দিনগুলোকে মনে করে লেখা হয়েছে। এই বই আমার একান্ত নিজস্ব জীবন দলিল বললেও হয়তো অত্যুক্তি হবে না। ... ...জীবন মানেই উৎসব, জীবন মানেই সম্ভাবনা। আপনার লেখাগুলো প্রতি মুহূর্তে সেই জীবনেরই জয়গান গেয়েছে। কাদামাটির হাফলাইফ জীবন থেকে শিক্ষা নিয়েই জীবনকে উপলব্ধি করতে শেখাবে, এই বিশ্বাস জারি থাকল। ... ...
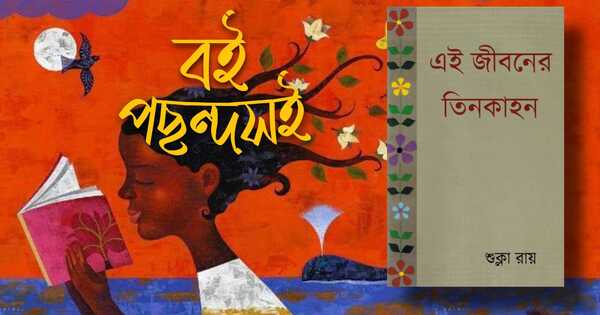
এই জীবনের তিনকাহন (শুক্লা রায়) - মালিনী সিদ্ধান্ত
বুলবুলভাজা | পড়াবই : বই পছন্দসই | ২১ এপ্রিল ২০২৪ | ৯৩৬ বার পঠিত | মন্তব্য : ৪, লিখছেন (অমিতাভ চক্রবর্ত্তী, মালিনী সিদ্ধান্ত , হীরেন সিংহরায়)এই জীবনের তিনকাহন-এর প্রথমপর্ব, ‘বাপের বাড়ি’। লেখিকার জন্ম ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে। রাসবিহারী অ্যাভিনিউ-এ বাড়ি। ঠাকুরদা, ঠাকুমা, বাবা, জ্যাঠা, কাকা, পিসি সকলে মিলে বিশাল এক যৌথ পরিবার। চন্দননগরে সংস্কৃত টোল পণ্ডিতের বংশগত জীবিকা ছেড়ে শিক্ষা-চাকরির জন্য ঠাকুরদার কলকাতায়ন। তারপরে কলকাতায় বাড়ি বানিয়ে পাকাপাকি ভাবে বসবাস। বাবা-কাকা-জ্যাঠারা স্ব-স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। কেউ ইঞ্জিনিয়ার, কেউ বা আইনজীবী। বাড়ি ভর্তি ভাই-বোনেরা, আর আছেন গোপালজিউ। সেইজন্য বাড়িতে আমিষ খাবারের প্রচলন নেই। ভাই-বোনেরা মিলে বাড়িটাকে পুরো মাতিয়ে রাখে। কখনও থিয়েটার, কখনও হাতে-লেখা পত্রিকা প্রকাশ, আবার কখনও বা নিখাদ দুষ্টুমি। সঙ্গে বিজয়া, দোল, ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার মতো চিরাচরিত উৎসব পালন তো লেগেই আছে। সেখানেও অবশ্য পারিবারিক বৈশিষ্ট্যের বিশেষ কিছু স্বাক্ষর আছে। অন্দরের অন্তর লেখিকার লেখায় এক নিরবচ্ছিন্ন চিত্রপটে ধরা দিয়েছে। ... ...
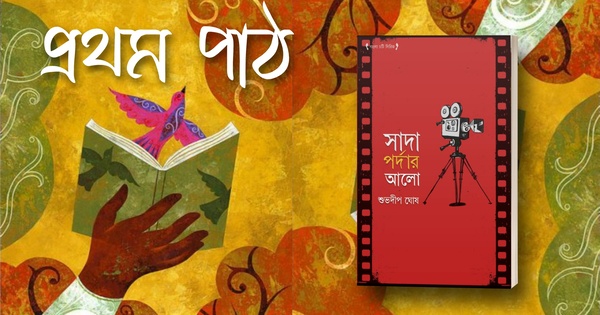
পুস্তক সমালোচনা : সাদা পর্দার আলো (শুভদীপ ঘোষ) - সোমনাথ ঘোষ
বুলবুলভাজা | পড়াবই : প্রথম পাঠ | ০১ এপ্রিল ২০২৪ | ১১০০ বার পঠিত | মন্তব্য : ৪, লিখছেন (রচয়িতা দত্ত, রমিত চট্টোপাধ্যায়, Amitava Mukherjee)শুভদীপের প্রবন্ধগুলি কিন্তু সেইসব চলচ্চিত্রকারদের নিয়ে যাদের কাজ শৈল্পিক ভাবে নিপুণ। শুভদীপের প্রবন্ধে যেমন আছেন গোদার, বার্গম্যান, আন্তনিওনি, হিচকক, চ্যাপলিন তেমনই আছেন কিয়ারোস্তামি, ওজু, আমাদের সত্যজিৎ, মৃণাল এবং বর্তমান সময়ের বিখ্যাত চলচ্চিত্রকার নুরি বিলজ সিলান। যে কোন সফল প্রাবন্ধিকের লেখনীর একটা নিজস্ব স্টাইল থাকে। শুভদীপের লেখনীর দুটি বৈশিষ্ট্য আছে। দ্বিতীয়টির কথায় আমরা একটু পরে আসছি। শুভদীপ কোন প্রবন্ধের শুরুতেই সাধারণত মূল বিষয়ে সরাসরি প্রবেশ করেন না। এখানে মূল বিষয় বলতে বলা হয়েছে চলচ্চিত্র বা চলচ্চিত্রকার সম্পর্কিত আলোচনা। লেখকের একাধিক প্রবন্ধই শুরু হয় কোন উদাহরণ/ উপমা বা কোন সংজ্ঞার ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ দিয়ে। যেহেতু প্রবন্ধগুলি সময়কাল অনুযায়ী সাজানো (বইয়ের সর্বপ্রথম প্রবন্ধ তার সাম্প্রতিকতম লেখা), তাই বোঝা যায় সময়ের সাথে লেখক এই স্টাইলটি রপ্ত করেছেন। ... ...
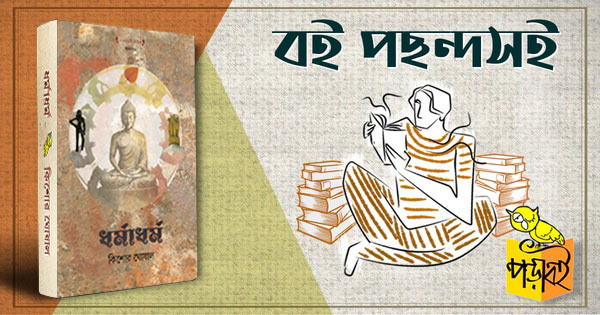
এতদিন যে বসেছিলেম - হীরেন সিংহরায়
বুলবুলভাজা | পড়াবই : বই পছন্দসই | ১৭ মার্চ ২০২৪ | ১০৪০ বার পঠিতদু বছর আগে গুরুচণ্ডালির পাতায় কিশোর ঘোষালের আগমন নয় আবির্ভাব হলো। এক বিদ্যুৎচমক। ক্রমশ তিনি আমার হাতে ধরে নিয়ে গেলেন, বর্তমানের আলোয় অতীতকে চেনালেন। সলতে না পাকালে সাঁঝবাতি জ্বলে না। তিনি সেই সলতে পাকানোর পর্বটি দেখালেন সযত্নে। আমার পৃথিবীকে চেনার জানার যে বিশাল ফাঁক ছিল, সেটিকে তিনি অবহিত করালেন, প্রতিটি লেখা পড়ে ভেবেছি – এতো দিন কোথায় ছিলেন? ... ...
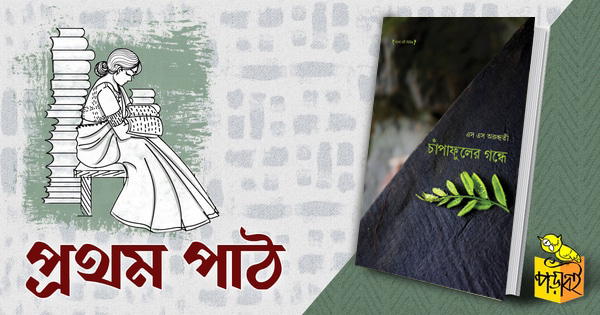
কালো কালো ছায়ারা - স্বাতী রায়
বুলবুলভাজা | পড়াবই : প্রথম পাঠ | ১০ মার্চ ২০২৪ | ৯৩২ বার পঠিত | মন্তব্য : ৫, লিখছেন (দীমু, অমিতাভ চক্রবর্ত্তী, Nupur Raychaudhuri)অরুন্ধতী নির্লিপ্ত ভাবে সাজিয়েছেন দশটি গল্প। মেয়েদের গল্প বলব নাকি জীবনের গল্প বলব সে প্রশ্নের মীমাংসা হয়নি এখনো। তবে সব কটি গল্পেই মেয়েরা তীব্র রকমের আছেন। খুব মোলায়েম ভাবে বলা, নিখুঁত ডিটেইলিং ওলা জীবন্ত দশটি গল্প। প্রতিটা গল্পেরই উপজীব্য জীবনের জটিল অন্ধকার এক একটা দিক । আর প্রায় প্রতিটা গল্প অব্যর্থসন্ধানী তীরন্দাজ। ... ...
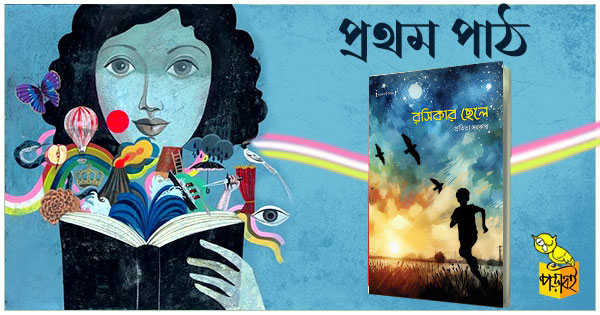
রসিকার ছেলে - দেবকুমার চক্রবর্তী
বুলবুলভাজা | পড়াবই : প্রথম পাঠ | ১০ মার্চ ২০২৪ | ৯৯৪ বার পঠিত | মন্তব্য : ১৫, লিখছেন (Suparna Bhattacherjee, Prativa Sarker, Prativa Sarker)প্রতিভা সরকার গল্প উপন্যাস লেখেন পাঠককে ভুলিয়েভালিয়ে মোহাবিষ্ট করে রাখতে নয়। চরিত্রগত ভাবে একজন পরিবেশ-কর্মী, মানবতাবাদী, নারীবাদী সংবেদনশীল লেখিকা হিসেবে পাঠককে ভাবিয়ে তোলাই প্রতিভার ‘হিডন এজেন্ডা’। সমাজের সমস্ত স্তরে জমাট বাঁধা অন্যায়ের বিরুদ্ধে পাঠক-সমাজকে মনে মনে আন্দোলনের ভাগীদার করে তোলাই প্রতিভার উদ্দেশ্য। ‘রসিকার ছেলে’ উপন্যাসে প্রতিভা সে ব্যাপারে সফল। ‘রসিকার ছেলে’ উপন্যাসটি দেশের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় অনুবাদ করা হলে সমাজবিজ্ঞানের কিছু উপকার হতে পারত। জাত-পাতের রাজনীতির বিরুদ্ধে জন-জাগরণে মৃদু তরঙ্গ উঠলেও উঠতে পারত। বইটির ইংরেজি অনুবাদ করবেন, প্রকাশ করবেন, বৃহত্তর আঙিনায় পাঠকের হাতে তুলে দেবেন – এমন প্রকাশনা সংস্থা কবে উদ্যোগ নেবে জানা নেই। এনবিটি বা সাহিত্য অকাদেমী কি এগিয়ে আসবে? ... ...
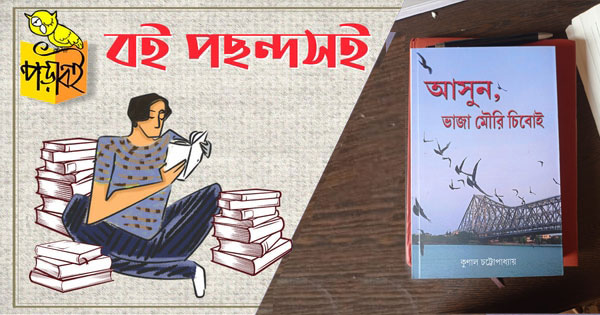
স্বচ্ছন্দ, নির্লিপ্ত আয়নায় সমকাল - হীরেন সিংহরায়
বুলবুলভাজা | পড়াবই : বই পছন্দসই | ০৩ মার্চ ২০২৪ | ৮৬৩ বার পঠিত | মন্তব্য : ২, লিখছেন (Kishore Ghosal, অমিতাভ চক্রবর্ত্তী)নিউ ইয়র্কে বলে, ইউ ক্যান টেক দি গার্ল আউট অফ ব্রনক্স বাট ইউ ক্যান নট টেক দি ব্রনক্স আউট অফ দি গার্ল। ভারমুক্ত আমি চলে এসেছি অনেক দূরে ইংল্যান্ডের সারেতে কিন্তু কুণালের লেখা মনে করিয়ে দিল, ‘ইউ ক্যান নট টেক বরানগর আউট অফ মি’। কুণাল আমার চেয়ে অনেক ছোটো হবেন, কিন্তু তিনি আর আমি দেখেছি এক আশ্চর্য উত্তাল সময়কে –দিকে দিকে ছড়ানো লাল আগুনের উত্তাল কলকাতা একাত্তর, সেখানে তিনি অর্থনীতি পড়ছেন, অমর্ত্য সেনের পভার্টি অ্যান্ড ফেমিনের কথা বলছেন আর তুষার রায়! রতন বাবু রোডের, আমাদের তুষারদার ব্যান্ডমাষ্টার অঙ্ক কষছেন ম্যাজিক লুকিয়ে চক এবং ডাস্টার। ... ...
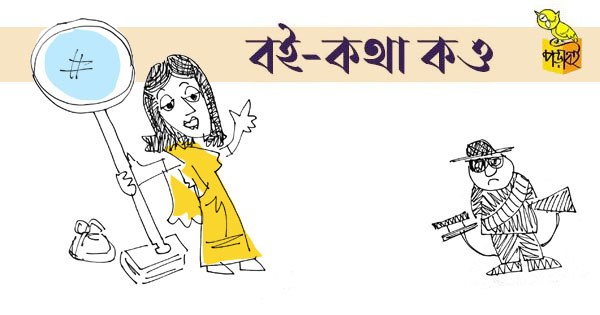
ঘরের বাইরে পা, গোয়েন্দাগিরিতেও তাক লাগান বাঙালি মেয়েরা - রণিতা চট্টোপাধ্যায়
বুলবুলভাজা | পড়াবই : বই কথা কও | ০৩ মার্চ ২০২৪ | ১১১০ বার পঠিত | মন্তব্য : ৩, লিখছেন (দ, kk, :|:)তবে বাংলা সাহিত্যে গোয়েন্দানীর উৎসে পাশ্চাত্যের ঋণ থাকলেও এ কথা মানতেই হবে, পিতৃতান্ত্রিক অপরাধ-সাহিত্যপরিসরে গোয়েন্দা হিসেবে নারীদের উঠে আসা একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা ছিল। আর এই উত্থান যে ধূমকেতুর মতো সহসা দেখা দিয়েই মিলিয়ে যাওয়ার মতো নয়, সে কথাও স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল তার পরবর্তী দুই দশকেই। তাই কৃষ্ণা-শিখার মতো অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় মাতোয়ারা সম্পন্ন তরুণী কিংবা বিন্দিপিসি-সদুঠাকুমার মতো ঘরোয়া বয়স্কা মহিলা নন, ক্রমশ এই দুনিয়ায় আসর জাঁকিয়ে বসতে শুরু করলেন সেই মেয়েরা, যাঁরা পেশাগতভাবেই গোয়েন্দাগিরি বা অন্য কোনও বৃত্তিকে অবলম্বন করেছেন। অজিতকৃষ্ণ বসুর ডিটেকটিভ নন্দিনী সোম সায়েন্স কলেজ থেকে এক্সপেরিমেন্টাল সাইকোলজির স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থানাধিকারিণী। ... ...
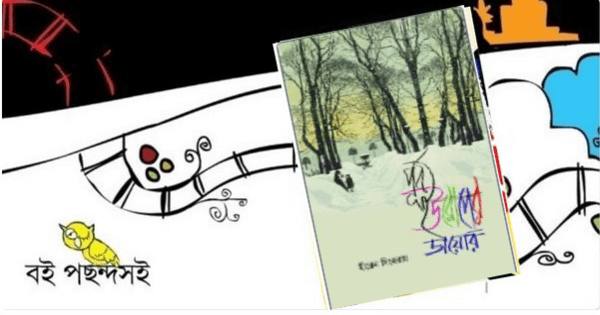
গল্পের ছলে ইতিহাসের দিনলিপি - ঋত
বুলবুলভাজা | পড়াবই : বই পছন্দসই | ১৪ জানুয়ারি ২০২৪ | ১৩১৫ বার পঠিত | মন্তব্য : ৮, লিখছেন ( Tapan Kumar SenGupta, ঋত, ঋত)ইতিহাসের বিশেষ সন্ধিক্ষণ ইতিহাসের মঞ্চে দাঁড়িয়ে পরখ করার সৌভাগ্য হয় ক’জনের! বৃত্তের বাইরে থেকে নয়, একেবারে কেন্দ্রে থেকে পটপরিবর্তনের সাক্ষী থাকা এবং তাকে লিপিবদ্ধ করা গল্প বলার ছলে, এ নিতান্ত সহজ কাজ নয়। পাঠ্যবইয়ের ‘ইতিহাস’-এর বাইরে বেরিয়ে যে ভাবে ঐতিহাসিক ঘটনা লেখক নিজে পরখ করেছেন, তার অভিঘাত যা নিজে চোখে দেখেছেন এবং বিশ্লেষণী মন নিয়ে অনুসন্ধান করেছেন, তা এই বইটিকে নিছক ভ্রমণ কাহিনী বা আত্মজৈবনিক অন্য কোনও রচনার থেকে পৃথক করেছে। এখানেই হীরেন সিংহ রায়ের পূর্ব ইউরোপের ডায়েরি স্বতন্ত্র। গুরুচণ্ডালী-তে যে লেখা ইতিপূর্বে ধারাবাহিক হিসাবে প্রকাশিত হত, তা-ই এ বার দু’মলাটের মধ্যে। ... ...
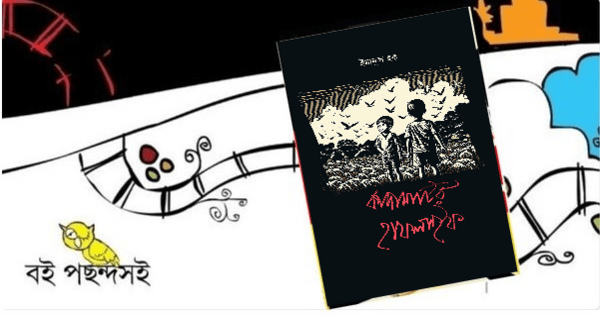
কাদামাটির হাফলাইফ - পাঠ প্রতিক্রিয়া - সুপান্থ বসু
বুলবুলভাজা | পড়াবই : বই পছন্দসই | ১৪ জানুয়ারি ২০২৪ | ৮০৫ বার পঠিত | মন্তব্য : ১, লিখছেন (তৌহিদ হোসেন)গাছের যে অংশ থাকে মাটির ওপরে তাই আমরা দেখি। অর্থাৎ কাণ্ড , শাখা, ডালপালা আর পাতা - ফুল - ফল। আর যা থাকে মাটির নীচে, সেটা অদৃশ্যগোচরই রয়ে যায়। যেমন, শিকড়। শিকড় সন্ধান করতে লাগে.... খুঁজলে পাওয়া যায়। আর না খুঁজলে, বিস্মৃতির অতলে। আমাদের আদত যাপন চিত্রের এক অনুপুঙ্খ ধারা - বিবরণ হিসেবে নয়, ধারণ করে রাখে যে সব পাতা, সে সব পাতাগুলো এক জায়গায় জড়ো করলে হয় ইতিহাস। ইমানুল হকের লেখা 'কাদামাটির হাফলাইফ' সে অর্থে ইতিহাস। ... ...
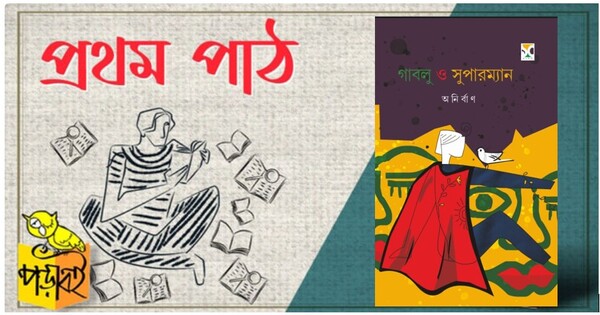
‘গাবলু ও সুপারম্যান’ - দেবারতি গুপ্ত
বুলবুলভাজা | পড়াবই : প্রথম পাঠ | ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ | ১০৪৪ বার পঠিত | মন্তব্য : ৪, লিখছেন (রমিত চট্টোপাধ্যায়, দ, r2h)“আকণ্ঠ কুয়োয় ডুবে আছে যে মানুষ সে জানে তার আকাশ বৃত্তাকার। তাকে দিগন্তরেখার লোভ দেখিও না।” পড়ে খটকা লাগলো যে আমার আকাশও কি বৃত্তাকার দেখছি বহুদিন? যে চিন্তা এতদিন টনক নড়ায় নি! স্মৃতি হাতড়ে মনে করার চেষ্টা করি আকাশের অন্য কোন আকার দেখেছিলাম কি না! কিন্তু এই স্মৃতিও খুব সহজে মনে পড়ার নয়। এ গত জন্মের আচ্ছন্নতা নিয়ে ইহজন্মে মাতৃ-জঠরে ভাসমান থাকার স্মৃতি। যা স্মৃতি আর বিস্মৃতির মাঝের গোধূলি! যা হৃদয়েরও যে একটি মস্তিষ্ক আছে, হৃদয় যার খোঁজ রাখে না, তাকে মনে করিয়ে দেয়। ... ...
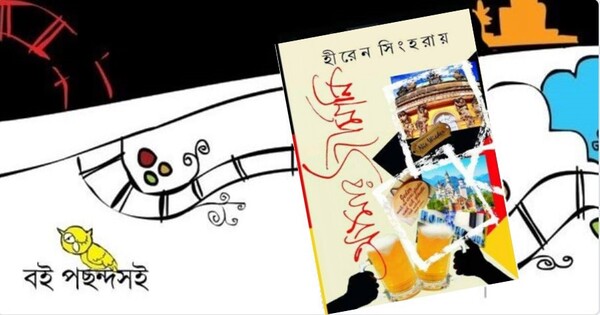
হীরেন সিংহ রায়-এর ‘আমার জার্মানি’ - একটি আলোচনা (দ্বিতীয় পর্ব) - মিলন দাস
বুলবুলভাজা | পড়াবই : বই পছন্দসই | ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ | ৯১১ বার পঠিত | মন্তব্য : ১, লিখছেন (আশীষ সিংহরায়।)বয়স্ক জার্মান ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, আমিই সেই জার্মান সৈনিক। ডেভিড সেটা বুঝলেন। কারও মুখে কোনো কথা নেই। উনচল্লিশ বছর আগে ইলিনয়ের ডেভিড দে ফ্রিস অস্ত্র হাতে জার্মানির হেসেনের এক পরাস্ত জার্মানের মুখোমুখি হয়েছিলেন। চারদিকে যখন খুন কা বদলা খুন হচ্ছে, সেখানে অস্ত্রহীন জার্মানকে সঙ্গে করে নিয়ে গেছেন তার ওপরওয়ালার অফিসে। তার পরিচয়পত্র নাম ইত্যাদি নথিবদ্ধ করে, তাকে যুদ্ধবন্দির সম্মান দেওয়া হয়েছে। যুদ্ধের শেষে বিজেতারা ফিরেছেন শিকাগো ইলিনয়, আর বিজিত ফিরেছেন হেসেন, জার্মানি। জার্মান ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন প্রথমে। ডেভিডও ততক্ষণে বেঞ্চ ছেড়ে উঠে পড়েছেন। চার দশক আগের দুই শত্রু। একে অপরকে আলিঙ্গন করলেন। ... ...
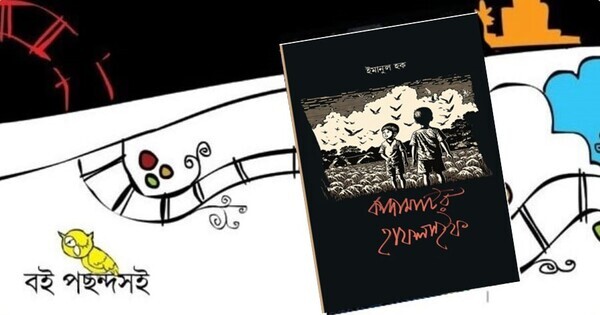
কাদামাটির হাফলাইফ: পুষ্পক সময়কে ফিরে ফিরে দেখা - আশরাফুল মণ্ডল
বুলবুলভাজা | পড়াবই : বই পছন্দসই | ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ | ৯৪৮ বার পঠিত | মন্তব্য : ১, লিখছেন (তৌহিদ হোসেন)'কাদামাটির হাফলাইফ' -- একটি অনন্যসাধারণ রচনা। অনন্যতা নামকরণে। হৃদয়ে বিরাজ করা ভাবনা নির্বাচনে। অনবদ্য জীবনকথা উচ্চারণে। বৈঠকি মেজাজে সত্যোচ্চারণ করার অভূতপূর্ব ভঙ্গিমায়। ১১৬ পর্বে বিন্যস্ত জীবনে জীবন যোগ করার অবিস্মরণীয় সাহিত্যকর্ম 'কাদামাটির হাফলাইফ' সাহিত্যকর্ম তো বটেই, অন্তত আমার নিবিড় পাঠ অনুভবে। বইটির প্রতিপাদ্য বিষয়ের সঙ্গে ষোলআনা একাত্মতায়। আমরা জানি কোনো প্রচারধর্মী, রাজনৈতিক, সামাজিক বা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য থেকে জাত হতেই পারে না প্রকৃত সাহিত্য। ভাবে ভাষায় ও রূপে তার নির্মাণ এক 'হয়ে ওঠার' বৃত্তান্ত। মার্কিন কবি আর্চিবল্ড ম্যাকলিশের কথায় : " A poem Should not mean / But be." ইমানুল হকের 'কাদামাটির হাফলাইফ' ঠিক তেমনই গ্রামবাংলার নির্ভেজাল ও 'কান্না হাসির দোল দোলানো পৌষ ফাগুনের পালা'-র সার্থক সাহিত্যরূপ। ... ...
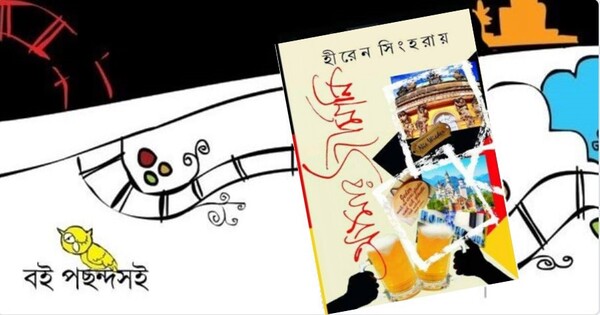
হীরেন সিংহ রায়-এর ‘আমার জার্মানি’ - একটি আলোচনা (প্রথম পর্ব) - মিলন দাস
বুলবুলভাজা | পড়াবই : বই পছন্দসই | ১৭ ডিসেম্বর ২০২৩ | ১২৬৩ বার পঠিত | মন্তব্য : ৪, লিখছেন (মোহাম্মদ কাজী মামুন, জয়, হীরেন সিংহরায়)খুবই গোলমেলে অ্যাসাইনমেন্ট। ‘আমার জার্মানি’ বইটার রিভিউ করতে বসেছি। গোদা বাংলায় পুনর্বার দেখা (Review) কি দেখব, কোনখান থেকে দেখব। শুধু জার্মানি হলে কথা ছিল। স্টেট ব্যাঙ্কের চাকরি ১৯৭২ সালে। জলপাইগুড়ি বহরমপুর শ্যামবাজার ব্রাঞ্চে কাজ শেখা। তিন বছর বাদে দু-বছরের জন্য জার্মানির ফ্রাঙ্কফুট অফিসে বদলি। ফ্রাঙ্কফুটের প্রথমদিন একটি অসামান্য অবদান। পুরো লেখাটার মধ্যে ছড়িয়ে আছে রসিকতার মণিমুক্ত। যে লেখক নিজের দুঃখ নিয়ে নির্মল রসিকতা করতে পারে তার লেখনি কোন মার্গে উঠতে পারে এই অধম রিভিউ রাইটার তা কল্পনাও করতে পারেননি। আসার সময় হাতে ছিল ১২৫ ডলার তার মধ্যে ৫৫ ডলার নিজের সুটকেসের লাইনিংয়ের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলেন। হাতে পেনসিলের মতো করে ধরা ছিল ৭০ ডলার। হীরেন পৌঁছে গেলেন ফ্রাঙ্কফুর্টে কিন্তু সুটকেস পৌঁছলো না। নিজের অসহায় অবস্থার বিবরণে যে স্যাটায়ার লুকিয়ে আছে, তা এককথায় নান্দনিক। ... ...
- পাতা : ১৮১৭১৬১৫১৪১৩১২১১১০৯
-
গুরুচণ্ডা৯-র গ্রাহক হোন
কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে গুরুচণ্ডা৯-র গ্রাহক হোন। গুরুচণ্ডা৯তে প্রকাশিত লেখাগুলি পেতে চাইলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যুক্ত হোন, অথবা, আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলটির গ্রাহক হোন।
- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই
- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... অমিতাভ চক্রবর্ত্তী)
(লিখছেন... কচ্ছপ, Debasis Bhattacharya, Debasis Bhattacharya)
(লিখছেন... অমিতাভ চক্রবর্ত্তী, মোহাম্মদ কাজী মামুন , Kishore Ghosal)
(লিখছেন... অমিতাভ চক্রবর্ত্তী, অভিজিৎ। , অমিতাভ চক্রবর্ত্তী)
(লিখছেন... হীরেন সিংহরায়, Rouhin Banerjee, R.K)
- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন
(লিখছেন... )
(লিখছেন... অসিতবরণ বিশ্বাস , দ)
(লিখছেন... দ)
(লিখছেন... aranya , হীরেন সিংহরায়, পাপাঙ্গুল)
(লিখছেন... r2h, Guru)
- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... :|:, রঞ্জন , :|:)
(লিখছেন... ., Guru, Guru)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... দীপ, দীপ , ar)
(লিখছেন... কৌতূহলী, Debasis Bhattacharya, কৌতূহলী)
- কি, কেন, ইত্যাদি
- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...
- আমাদের কথা
- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...
- বুলবুলভাজা
- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...
- হরিদাস পালেরা
- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...
- টইপত্তর
- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...
- ভাটিয়া৯
- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...
- বুলবুলভাজা গুরুচন্ডা৯-র সম্পাদিত বিভাগ। এই বিভাগে প্রকাশিত লেখা অন্যত্র প্রকাশের ক্ষেত্রে গুরুচণ্ডা৯ ও লেখকের অনুমতি ও উল্লেখ প্রয়োজনীয় । টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই । ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত ।


