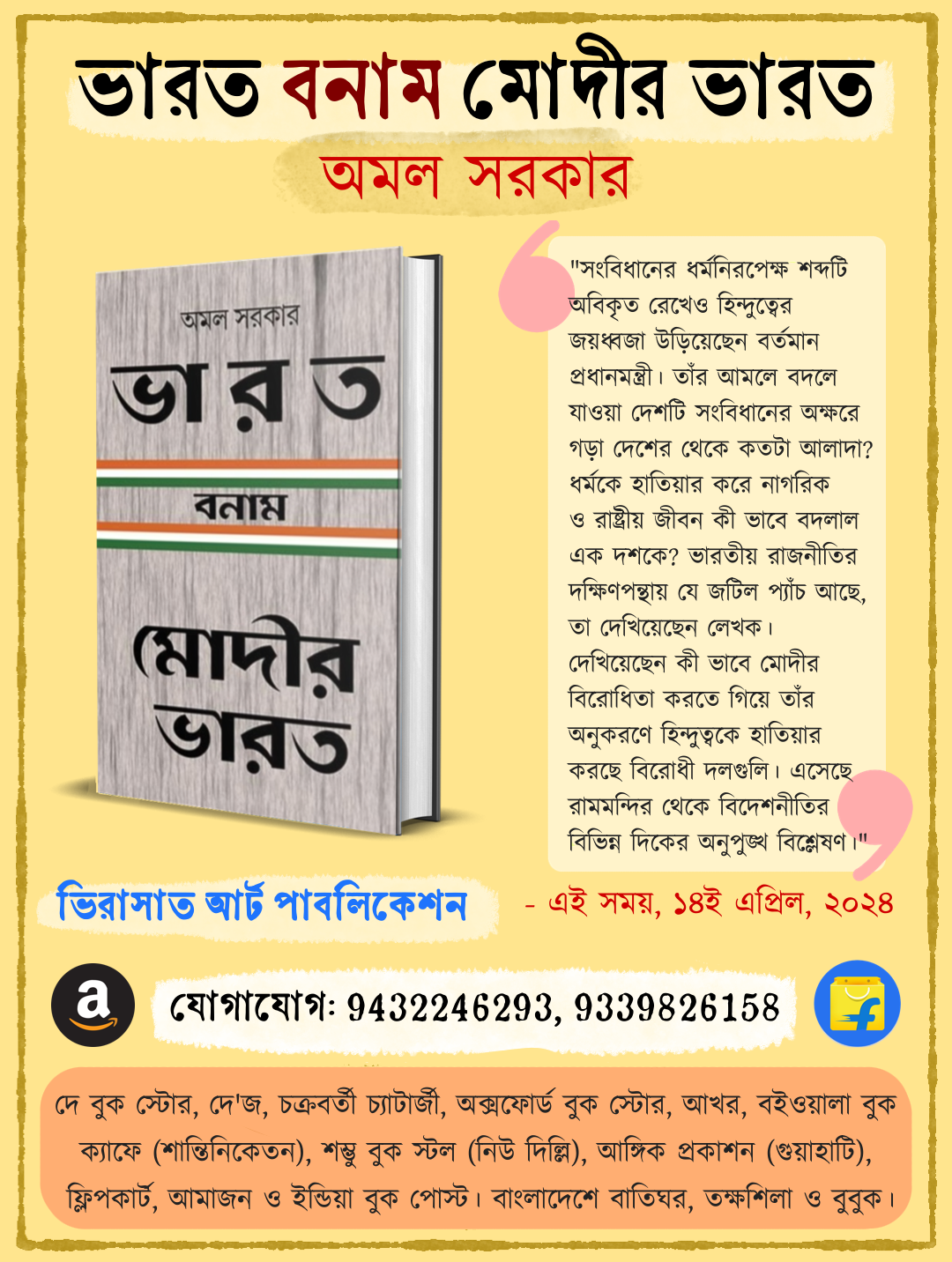- টইপত্তর অন্যান্য

-
ঝড়বিষ্টির গল্প
Achintyarup Ray
অন্যান্য | ২২ মার্চ ২০১১ | ৮৪৪৬♦ বার পঠিত
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
 achintyarup | 59.93.244.111 | ২২ মার্চ ২০১১ ০২:৫৬468855
achintyarup | 59.93.244.111 | ২২ মার্চ ২০১১ ০২:৫৬468855- ঘিলু ভেস্তিয়ে থাকার কারণে বুদ্ধি গজাচ্চে না এবং নতুন লেখাও বেরুচ্চে না। সোজা উপায় হল পুরোনো লেখা স্যাটাস্যাট টুকে দেওয়া। তা ছাড়া কালবোশেখীর সিজিনও এসে গেল, এই তালে এ লেখাটা চালিয়ে দেওয়া যায়।
(এখন যে লেখা পুন:পরিবেশন করতে যাচ্ছি, সেইটে বছর তিনেক আগে টাইম্স অব ইণ্ডিয়ার আমার সময় নামক বাংলা সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছিল)
 achintyarup | 59.93.244.111 | ২২ মার্চ ২০১১ ০৩:০০468866
achintyarup | 59.93.244.111 | ২২ মার্চ ২০১১ ০৩:০০468866- নিজের লেখার সঙ্গে অন্য লোকেদের লেখাও খানিক টুকে দেব ঠিক করলাম।
 achintyarup | 59.93.244.111 | ২২ মার্চ ২০১১ ০৩:০৮468877
achintyarup | 59.93.244.111 | ২২ মার্চ ২০১১ ০৩:০৮468877- অমাবস্যার রাত্তির -- অন্ধকারে ঘুরঘুট্টি -- গুড় গুড় করে মেঘ ডাক্চে -- থেকে থেকে বিদ্যুৎ নল্পাচ্চে -- গাছের পাতটি নড়্চে না -- মাটী থেকে যেন আগুনের তাপ বেরুচ্চে -- পথিকেরা এক একবার আকাশপানে চাচ্চেন আর হন্ হন্ করে চলেচেন -- কুকুরগুলো খেউ খেউ কচ্চে... গির্জ্জের ঘড়িতে ঢং ঢং ঢং করে দশটা বেজে গ্যালো, সোঁ সোঁ করে একটা বড় ঝড় উঠ্লো -- রাস্তার ধূলো উড়ে যেন অন্ধকার আরো বাড়িয়ে দিলে -- মেঘের কড় মড় কড় মড় ডাক ও বিদ্যুতের চকমকিতে ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলেরা মার কোলে কুণ্ডুলি পাকাতে আরম্ভ কল্লে -- মুসলের ধারে ভারী এক পসলা বিষ্টি এলো।
-- হুতোম প্যঁচার নকশা (১৮৬২)
 achintyarup | 59.93.244.111 | ২২ মার্চ ২০১১ ০৩:২০468888
achintyarup | 59.93.244.111 | ২২ মার্চ ২০১১ ০৩:২০468888- নগেন্দ্র প্রথম দুই এক দিন দেখিতে দেখিতে গেলেন। পরে একদিন আকাশে মেঘ উঠিল, মেঘ আকাশ ঢাকিল, নদীর জল কালো হইল, গাছের মাথা কটা হইল, মেঘের কোলে বক উড়িল, নদী নিস্পন্দ হইল। নগেন্দ্র নাবিকদিগকে আজ্ঞা করিলেন, ""নৌকাটা কিনারায় বাঁধিও।'' রহমত মোল্লা মাঝি তখন নেমাজ করিতেছিল, কথার উত্তর দিল না। ... নেমাজ সমাপ্ত হইলে বাবুর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, ""ভয় কি হুজুর! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।''... বোধ হয়, রহমত মোল্লার সঙ্গে দেবতার কিছু বিবাদ ছিল, ঝড় কিছু গুরুতর বেগে আসিল। ঝড় আগে আসিল। ঝড় ক্ষণেক কাল গাছপালার সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করিয়া সহোদর বৃষ্টিকে ডাকিয়া আনিল। তখন দুই ভাই বড় মাতামাতি আরম্ভ করিল। ভাই বৃষ্টি, ভাই ঝড়ের কাঁধে চড়িয়া উড়িতে লাগিল। দুই ভাই গাছের মাথা ধরিয়া নোয়ায়, ডাল ভাঙ্গে, লতা ছেঁড়ে, ফুল লোপে, নদীর জল উড়ায়, নানা উৎপাত করে। এক ভাই রহমত মোল্লার তুপি উড়াইয়া লইয়া গেল, আরেক ভাই তাহার দাড়িতে প্রস্রবণের সৃজন করিল। দাঁড়ীরা পাল মুড়ি দিয়া বসিল।
বিষবৃক্ষ (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ১৮৭২)
 achintyarup | 59.93.244.111 | ২২ মার্চ ২০১১ ০৩:৩১468899
achintyarup | 59.93.244.111 | ২২ মার্চ ২০১১ ০৩:৩১468899- কাল পনেরো মিনিট বাইরে বসতে না বসতে পশ্চিমে ভয়ানক মেঘ করে এল। খুব কালো গাঢ় আলুথালু রকমের মেঘ... খানিক বাদে একটা আক্রোশের গর্জন শোনা গেল; কতগুলো ছিন্নভিন্ন মেঘ ভগ্নদূতের মত সুদূর পশ্চিম থেকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এল -- তার পরে বিদ্যুৎ বজ্র ঝড় বৃষ্টি সমস্ত একসঙ্গে এসে পড়ে খুব একটা তুর্কি-নাচন নাচতে আরম্ভ ক'রে দিলে। বাঁশগাছগুলো হাউহাউ শব্দে একবার পূর্বে একবার পশ্চিমে লুটিয়ে লুটিয়ে পড়তে লাগল, ঝড় যেন সোঁ সোঁ ক'রে সাপুড়ের মত বাঁশি বাজাতে লাগল, আর জলের ঢেউগুলো তিন লক্ষ সাপের মতো ফণা তুলে তালে তালে নৃত্য আরম্ভ ক'রে দিলে... বজ্রের যে শব্দ সে আর থামে না, আকাশের কোন্খানে যেন একটা আস্ত জগৎ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাচ্ছে।'
-- ছিন্নপত্র (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৮৯১)
 achintyarup | 59.93.244.111 | ২২ মার্চ ২০১১ ০৩:৪২468910
achintyarup | 59.93.244.111 | ২২ মার্চ ২০১১ ০৩:৪২468910- জীমূতমন্দ্র বা অম্বরে ডম্বরু:
বদর বদর।
দরিয়ার পীরের নাম করে শুরু করা গেল ঝড় বাদলের বৃত্তান্ত। বলে নাকি নদীর ধারে বাস, ভাবনা বারো মাস। তা আমাদের নদীই বা কি, আর সাগরই বা কি। শহর কলকাতাই বল, কি দখিন বাংলার গাঁ-গেরাম -- সমুদ্দুর থেকে কতটুকুই বা দূর। সাগরের ক্ষ্যাপা হাওয়া আর কালো মোষের মত বর্ষার মেঘ একবার ধেয়ে এল তো আর কথা নেই। সবকিছু উড়িয়ে ফুরিয়ে ডুবিয়ে ভাসিয়ে একাকার করে নিয়ে যাবে একেবারে। এ আর নতুন কি খবর? সে কথা নতুন করে শোনানোরই বা আছে কি?
তবে পুরোনো কথা বলতেও মানা নেই কোনো। আর সেই কথাই এখানে বলতে বসা। সেকালের ঝড় বাদলের গপ্প।
হাওয়া আপিসের পুরোনো খাতা খুলে বসলেই দেখা যাবে সেখানে বড় বড় বেশ কিছু ঝড়ের কথা লেখা আছে। অতসব লেখার জায়গা মিলবে না এখানে। তাই তাদের থেকে ডাঙর ডাঙর গোটা দুই তিন বেছে নেওয়া। আর সাথে সাথে দুটো আশ কথা পাশ কথা।
 achintyarup | 59.93.244.111 | ২২ মার্চ ২০১১ ০৪:২০468921
achintyarup | 59.93.244.111 | ২২ মার্চ ২০১১ ০৪:২০468921- ঈশানের পুঞ্জমেঘ : ১৭৩৭
১৭৩৮ সালের জুন মাসে, বিলেতের জেণ্টলম্যান্স্ ম্যাগাজিনের আধখানা পাতা জুড়ে বঙ্গদেশের এক ভয়াবহ তুফানের কাহিনী প্রকাশিত হল। তাতে লেখা: "গত ৩০শে সেপ্টেম্বর (জুলিয়ান ক্যালেণ্ডার অনুযায়ী। ব্রিটিশ কলকাতায় সদ্য চালু হওয়া গ্রেগরিয়ান ক্যালেণ্ডারের হিসাবে এই ঝড় এসেছিল অক্টোবর মাসের ১১ তারিখ মাঝরাতে -- অচিন্ত্য) বঙ্গোপসাগরে এক প্রবল তুফান ওঠে। সঙ্গে প্রচণ্ড বৃষ্টি (ছয় ঘণ্টায় ১৫ ইঞ্চি) এবং ভয়ানক ভূমিকম্প। সে ভূকম্পের ধাক্কায় আর ঝড়ের দাপটে বহু বাড়ি ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে। গঙ্গানদীর উজানে ৬০ লীগ (প্রায় ৩০০ কিলোমিটার) পর্যন্ত প্রায় ২০,০০০ জাহাজ, বজরা, নৌকা ও ডিঙ্গি বিনষ্ট হয়েছে সেই প্রচণ্ড তুফানে। অগণ্য গবাদি পশু, বহু বাঘ এবং বেশ কয়েকটি গণ্ডার ঝঞ্ঝাস্ফীত নদীর জলে ডুবে মারা পড়েছে। জলের চাপে দমবন্ধ হয়ে প্রাণ হারিয়েছে অসংখ্য কুমীর এবং হাওয়ার ঝাপটায় অগণন সংখ্যক পাখি নদীতে পড়ে মারা গেছে। ৫০০ টনের দুখানি বিলাতি জাহাজ নদী থেকে ২০০ ফ্যাদম (৩০৯ মিটার) দূরে এক গ্রামের ভেতরে আছড়ে পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। জাহাজের যাত্রীরা ছিটকে গিয়ে পড়েছে গ্রামের মানুষজন এবং গরুমহিষের মাঝখানে। তাদের সকলেই জলে ডুবে মারা গেছে। বেশ কয়েকটি ৬০ টনের পালতোলা ছোট জাহাজ উড়ে গিয়ে নদী থেকে দুই লীগ দূরে গাছপালার মগডালের ওপর পড়েছে। নদীর জল স্বাভাবিকের থেকে প্রায় ৪০ ফুট বেশী ওপর দিয়ে বয়েছে বলে জানা গেছে। ডেকার, ডেভনশায়ার এবং নিউকাস্ল্ নামের তিনটি বিলাতি জাহাজ তীরে ধাক্কা খেয়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। পেলহ্যাম নামের আরেকটি জাহাজের কোনো খোঁজ পাওয়া যায় নি।
"একটি ফরাসী জাহাজ পাড়ের ওপর অনেকখানি পর্যন্ত উঠে গিয়েছিল। ঝড়-জল একটু কমলে মালপত্র বের করে আনার জন্য একজন মাল্লা জাহাজের খোলের ভেতর গিয়ে ঢুকেছিল। কিন্তু খানিক বাদেই সে লোকটি কাজ বন্ধ করে দিল। অনেকবার ডাকাডাকি করেও কোনো জবাব না পাওয়ায় অবশেষে আরেকজন মাল্লাকে ভেতরে পাঠানো হল। কিন্তু ভেতরে ঢোকার পর তারও আর কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। তখন সকলে খুব ভয় পেয়ে গেল। বেশ খানিকক্ষণ আর কেউই জাহাজের দিকে এগোতে রাজি হল না। অনেকক্ষন পরে বাকিদের থেকে শক্তিশালী একজন মাল্লা আস্তে আস্তে খোলের মধ্যে গিয়ে ঢুকল। কিন্তু বাকি দুজনের মতই তার কাছ থেকেও কোনো আওয়াজ পাওয়া গেল না। ব্যাপার দেখে উপস্থিত সকলে একেবারে হতভম্ব। তারপর অবশেষে মশাল নিয়ে দেখতে যাওয়া হল কী রহস্য লুকিয়ে আছে জাহাজের ভেতর। আলো ফেলতে দেখা গেল খোলের ভেতরটা জলে থইথই করছে, আর তার মাঝে শুয়ে রয়েছে প্রকাণ্ড এক কুমীর; যেন আরও শিকার পাওয়ার আশায় চেয়ে রয়েছে ওপরের দিকে। জাহাজের গায়ের একটা গর্তের মধ্যে দিয়ে প্রাণীটা ভেতরে গিয়ে ঢুকেছিল। বহু কষ্টে কুমীরটাকে মারার পর তার পেটের ভেতরে তিনজন মাল্লার দেহাবশেষ পাওয়া গেল।'
 achintyarup | 59.93.244.111 | ২২ মার্চ ২০১১ ০৪:৩৪468932
achintyarup | 59.93.244.111 | ২২ মার্চ ২০১১ ০৪:৩৪468932- প্রায় একই রকম বিবরণ পাওয়া যায় লণ্ডন ম্যাগাজিনেও। ১৭৩৮ সালের মে মাসের ঐ পত্রিকায় লেখা হয়েছিল: Friday 26 May 1738. The Bedford from the E. Indies brought advice of a most terrible Hurricane at Bengal, which demolished many Houses, killd vast numbers of Inhabitants and destroyed and damagd several of our East India ships
We had the following Particulars (among others) of the dreadful Hurricane that happend in India In the night between 11th and 12th Oct. last, there happened a furious Hurricane at the mouth of the Ganges, which reached 60 leagues up the River. There was at that same Time a violent Shock of an earthquake, which threw down a great many Houses along the River Side; in Golgota (কলকাতা) alone, a Port belonging to the English, 200 Houses were thrown down; and the high and magnificent Steeple of the English Church (সেণ্ট অ্যান্স্ চার্চ) sunk into the ground without breaking. It is computed that 20,000 Ships, Barks, Sloops, Boats, Canoes &c. have been cast away. Of 9 English ships then in the Ganges, 8 were lost and most of the Crews drowned. Barks of 60 tons were blown two leagues up into the Land, over the tops of high Trees. Of the 4 Dutch Ships in the river, 3 were lost, with all the Men and Cargoes. 300,000 souls are said to have perished. The Water rose forty Feet higher than usual in the Ganges.
এই দুই পত্রিকার সম্পাদকরা মোটামুটি একই ধরণের সূত্র থেকে ঝড়ের খবর পেয়েছিলেন বলে মনে হয়। পুবদেশ থেকে ফেরা জাহাজী মাল্লাদের মুখে মুখে তখন এই তুফানের কথা। কিন্তু দুটি পত্রিকার একটিতেও কোনো সরকারী সূত্র উল্লেখ করা হয়নি। তা করলে প্রকাশিত বিবরণ হয়ত অন্য রকম হত। সে কথায় পরে আসছি।
 achintyarup | 59.93.244.111 | ২২ মার্চ ২০১১ ০৫:১০468943
achintyarup | 59.93.244.111 | ২২ মার্চ ২০১১ ০৫:১০468943- পরবর্তীকালে Oldhams Catalogue of Indian Earthquake (1883) এই দুর্যোগের কথা উল্লেখ করে লিখেছেন পৃথিবীর সবচেয়ে বিধ্বংসী তিনটি ভূমিকম্পের মধ্যে একটি হয়েছিল ঐ ১৭৩৭-এর অক্টোবর মাসে, কলকাতা শহরে। ১৮৩৩-এর India Gazette-এও এই "ভয়াবহ ভূকম্পের' কথা লেখা হয়েছে। লেখা হয়েছে তিন লক্ষ মানুষের মৃত্যুর কথা।
এখন, যা রটে তার কতক বটে; কিন্তু সবটুকু নয়। আধুনিক ভূমিকম্প বিশারদরা প্রমাণ করে দিয়েছেন ১৭৩৭ সালের অক্টোবর মাসে (পুরোনো ক্যালেণ্ডারের হিসেবে সেপ্টেম্বর) কলকাতায় আদৌ কোনো ভূকম্পন হয়নি। সমকালীন সরকারী তথ্য এবং অন্যান্য প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনায় ভূমিকম্পের কোনো উল্লেখই পাওয়া যায় না। কলোরাডো ইউনিভার্সিটির ভূকম্পবিদ রজার বিলহ্যাম লিখেছেন, ঝড়ের সময় সেণ্ট অ্যান্স্ চার্চের কাঠের চূড়া যদিও ভেঙ্গে পড়েছিল, কিন্তু ঐ গির্জার মূল কাঠামোর অথাবা আর্মেনিয়ান চার্চ কি ফোর্ট উইলিয়ামের কোনো ক্ষতিই হয়নি। সত্যি সত্যিই জদি সেরকম ভয়াবহ কোনো ভূকম্পন ঐ দিন কলকাতায় হত,তাহলে এই ধরণের বড় বড় ইমারতগুলিই ক্ষতিগ্রস্ত হত সবচেয়ে বেশী। তার পরিবর্তে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে অসংখ্য খড়ের এবং মাটির দেওয়ালের হালকা বাড়ি। এর থেকে বোঝা যায় যে বিধ্বংসী ভূমিকম্প নয়, ঐ দিন কলকাতায় যা হয়েছিল তা হল এক মারাত্মক ঝড়। এবং সেই ঝড়ে তিন লক্ষ লোক নিহত হওয়ার খবরও খুবই অতিরঞ্জিত। কারণ সে সময়ে কলকাতার জনসংখ্যাই ছিল তার চেয়ে ঢের কম। ঝড়ের মাত্র দশ বছর আগে, ১৭২৭ সালে, আলেক্সাণ্ডার হ্যামিল্টন তাঁর A New Account of the East Indies বইতে শহর কলকাতার জনসংখ্যা দশ থেকে বারো হাজারের মধ্যে বলে উল্লেখ করেছেন। এমনকি ১৭৫৭ সালে কলকাতার প্রথম সরকারি জনগণনায় দেখা গেছে শহরের জনসংখ্যা মাত্র ৪৫,০০০। এইসব হিসেব মিলিয়ে পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করেছেন ১৭৩৭ সালে শহরে খুব বেশী হলে ২০,০০০ লোক বাস করত। ফলে তিন লক্ষ মানুষ মারা যাওয়ার ব্যাপারটা একেবারেই অবাস্তব। সেণ্ট অ্যান্স্ চার্চের রেজিস্টারেও দেখা গেছে ১৭৩৭ সালে শহরে সর্বমোট ১০৪ জন খৃষ্টানকে কবরস্থ করা হয়েছিল। গির্জার খাতায় তার আগে পরের দশ বছরের হিসেবের গড় নিয়ে দেখা গেছে এই সংখ্যা তার থেকে ২১ শতাংশ মাত্র বেশী।
এবার প্রত্যক্ষদর্শীদের রেখে যাওয়া বিবরণের কথায় আসা যাক। সে সময় কলকাতায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানির জমিদার ছিলেন টমাস জশুয়া মুর। কোম্পানির কাছে পাঠানো তাঁর ২৬শে অক্টোবরের রিপোর্টে মুর সায়েব লিখেছেন, ঝড়ের ধাক্কায় নেটিব ব্ল্যাক টাউনের অধিবাসীরা একেবারে সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছে। "খুব বেশী হলে গোটা বিশেক খোড়ো ঘর কোনোরকমে দাঁড়িয়ে আছে,' লিখেছিলেন সাহেব। কোম্পানির বড়কর্তাদের কাছে খাজনা মকুবের আবেদন জানিয়েছিলেন তিনি। কারণ, হাওয়ার তোড়ে নদীর জল ফুলে উঠে ভাসিয়ে দিয়ে গিয়েছিল সমস্ত চাষের জমি। বিঘার পর বিঘা ক্ষেতের ধান নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। অসংখ্য গবাদি পশু এবং পোষা হাঁস-মুরগী মারা পড়েছিল। কত মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল সেটাও তাঁর রিপোর্টে পরিষ্কার লিখেছিলেন মুর : near 3000 inhabitants were killed। কোম্পানির কতগুলি ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল তারও খতিয়ান দিয়েছেন সাহেব। There is great damage to the Companys Out guards of the Towns, the Publick Catcherry, the Gates of the Town and several other
places। এই রিপোর্ট লেখার দু দিন পরে, অক্টোবরের ২৮ তারিখে, হিসেব করে দেখা গেল সব মিলিয়ে কোম্পানির ৩২টি বাড়ির ভাল রকম ক্ষতি হয়েছে ঝড়ে। তাদের মধ্যে ২৪টি-কে আবার নতুন করে তৈরি করতে হবে। শহরের ২২টি গেটের মধ্যে ১৪টি টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে গেছে।
গোবিন্দরাম মিত্রের প্রতিষ্ঠিত কুমারটুলির বিশাল নবরত্ন মন্দিরটিও ভেঙ্গে পড়েছিল এই ঝড়ে। ৫৫ মিটার উঁচু সেই মন্দির সেকালের সাহেবদের কাছে ব্ল্যাক প্যাগোডা নামে পরিচিত ছিল।
বেশীরভাগ জমির ফসল নষ্ট হওয়ায় ঝড়ের পর পরই দেখা দিল মারাত্মক দুর্ভিক্ষ। কোম্পানি শহর থেকে বাইরে চাল নিয়ে যাওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা বসালেন এবং বছরখানেকের জন্যে চাল বিক্রির ওপর থেকে কর তুলে নেওয়া হল।
 siki | 123.242.248.130 | ২২ মার্চ ২০১১ ০৮:৩২468856
siki | 123.242.248.130 | ২২ মার্চ ২০১১ ০৮:৩২468856- গুড স্টার্ট। এইটা খুব ভালো টপিক।
 M | 59.93.198.82 | ২২ মার্চ ২০১১ ০৯:১৩468857
M | 59.93.198.82 | ২২ মার্চ ২০১১ ০৯:১৩468857- বেশ ভালো!!!!!!
 kumu | 122.162.176.161 | ২২ মার্চ ২০১১ ২২:৫১468858
kumu | 122.162.176.161 | ২২ মার্চ ২০১১ ২২:৫১468858- খুব ইন্টারেস্টিং লাগলো ।১৭৩৭ সালের প্রাকৃতিক বিপর্যয়,যাকে India Gazette উল্লেখ করেছে ভুমিকম্প বলে, তা আসলে ছিল এক বিধ্বংসী ঝড়?
৫-১০ এমের পোস্টে যা লেখা হয়েছে, তা অচিন্ত্যর নিজের গবেষণা?খুবই আগ্রহ জাগানো লেখা।
 dri | 117.194.239.92 | ২২ মার্চ ২০১১ ২৩:৪৮468859
dri | 117.194.239.92 | ২২ মার্চ ২০১১ ২৩:৪৮468859- অচিন্ত্যকে প্রশ্ন: সোর্সগুলো জোগাড় করলেন কিকরে? এই ধরণের সোর্সে অ্যাকসেস পাওয়ার আমার ইচ্ছে আছে।
১৭৩৮ সালের জুন মাসের জেন্টলম্যান্স ম্যাগাজিন
১৭৩৮ সালের মে মাসের লন্ডন ম্যাগাজিন
১৮৩৩ এর ইন্ডিয়া গেজেট
ওল্ডহ্যাম্স ক্যাটালগ অফ ইন্ডিয়ান আর্থকোয়েক
এবং সর্বোপরি
টমাস মুরের রিপোর্ট।
 achintyarup | 59.93.241.106 | ২৩ মার্চ ২০১১ ০৫:২৩468860
achintyarup | 59.93.241.106 | ২৩ মার্চ ২০১১ ০৫:২৩468860- @ কুমুদিদি: প্রমথনাথ বিশীর সম্পর্কে একটা চুটকি গল্প পড়েছিলাম। সত্যি কি মিথ্যে জানিনা। খানিকটা ভুলেও গিয়ে থাকতে পারি। ভদ্দরলোককে নাকি একবার প্রশ্ন করা হয়েছিল, আপনি তো অধ্যাপনাও করেছেন, সাংবাদিকতাও করেছেন। তো, এই দুটি পেশার বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু বলুন না। প্রনাবি নাকি জবাব দিয়েছিলেন, অধ্যাপনা করতে গিয়ে দেখেছি পণ্ডিতের মূর্খতা এবং সাংবাদিকতা করতে গিয়ে দেখেছি মূর্খের পাণ্ডিত্য।
খপরের কাগজে কাজ করতে করতে প্রতিদিন প্রমথবাবুর বক্তব্যের সত্যতার প্রমাণ পাই। তাই কুমুদিদিকে বলি, সাংবাদিকের লেখার মধ্যে কোনো গভীর গবেষণার খোঁজ করতে যেওনি কো। এই পোবন্ধে যা লেখা আছে, খানিকটে ধৈর্য এবং সময় নিয়ে বসলে গুরুর যে কোনো লেখক এবং পাঠক ওরকম মাল গণ্ডায় গণ্ডায় নামাতে পারবে বলে মনে করি।
@ dri: যে সব পত্র-পত্রিকা, বই এবং রিসার্চ পেপার থেকে এই লেখাটা টুকেছি সে সবই এই অন্তর্জাল থেকে পাওয়া। এক বারের জন্যেও কোনো লাইব্রেরিতে যাইনি।
জেণ্টলম্যান'স ম্যাগাজিন ইত্যাদির দরকারি ইস্যুগুলো তো নেট থেকেই নামিয়েছিলুম। আর গুগল বুকস তো স্বর্ণখনি বিশেষ।
একেবারে শেষে লিখব ভেবেছিলুম, কিন্তু বই এবং কাগজপত্তরের লিস্টিটা মাঝখানেই বলে দিই।
GENTLEMANS MAGAZINE (JUNE 1738)
LONDON MAGAZINE (JUNE 1738)
REPORT ON THE CALCUTTA CYCLONE OF THE 5TH OCTOBER, 1864
A BRIEF HISTORY OF THE CYCLONE AT CALCUTTA AND VICINITY, 5TH OCTOBER 1864 (1865)
THE SATURDAY MAGAZINE (1834)
MASSEY MONTAGUE, RECOLLECTIONS OF CALCUTTA FOR OVER HALF A CENTURY (1918)
BILHAM ROGER, THE 1737 CALCUTTA EARTHQUAKE AND CYCLONE EVALUATED (1984)
১৭৩৭-এর ঝড়ের অনেক কথা রজার বিলহ্যামের ফাটাফাটি পেপার থেকে একেবারে টুকে দিয়েছি। মুর সায়েবের কথাও মনে হয় ওখান থেকেই তুলেছিলাম। আরও সব আছে, ক্রমশ প্রকাশ্য।
 achintyarup | 59.93.241.106 | ২৩ মার্চ ২০১১ ০৫:৪৮468861
achintyarup | 59.93.241.106 | ২৩ মার্চ ২০১১ ০৫:৪৮468861- আরও যে কয়টি প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ পাওয়া যায় এই ঝড়ের (১৭৩৭), তার একটি লিখে গেছেন অলিভার ক্রমওয়েলের প্রপৌত্র সার ফ্রান্সিস রাসেল : "সে রাতের মত ভয়ঙ্কর ব্যাপার আমি আর কখনো দেখিও নি, শুনিও নি। বাতাসের এমন আওয়াজ যে মনে হয় যেন বাজ পড়ছে। তার সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি। শহরের সব চেয়ে পোক্ত বাড়ি আমার, তবুও মনে হচ্ছিল যে কোনো মুহূর্তে হুড়মুড় করে ছাদশুদ্ধ ভেঙ্গে পড়বে মাথার ওপর। বাতাসের শব্দ একটা সময় এমন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল যে দোতলায় আর থাকতে পারলাম না। সপরিবার একতলায় নেমে এসে বেচারি মিসেস ওয়াস্টেল আর তার বাচ্চাদের সঙ্গে রাতটা কাটালাম। ওয়াস্টেলদের বাড়ির সমস্ত দরজা-জানালা ভেঙ্গে উড়ে চলে গিয়েছিল বলে ওরা আমার এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। পরদিন সকালবেলায় উঠে শহর আর নদীর যে চেহারা দেখলাম সে আর কি বলব। আগের সন্ধ্যায় যে নদীতে ছোটবড় মিলিয়ে অন্তত ঊনত্রিশটা জাহাজ-নৌকো ভাসছিল, সেখানে ডিউক অব ডর্সেট ছাড়া আর কিচ্ছু নেই। বাকি অনেকগুলো আছড়ে পড়েছে পাড়ের ওপর, বেশ কয়েকটা একেবারে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে, আর কয়েকটা এদিক-ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে। আরেকটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার হল, প্রায় মাইলখানেক চওড়া নদীতে একটানা ২৪ ঘণ্টা ভাঁটা বলে কিছু ছিল না। আমাদের গির্জার চুড়োটাও পড়ে গিয়েছিল ঝড়ে। শহরের ইংরেজদের গোটা আট-দশ বাড়ি ভেঙ্গেছিল, বহু দিশি ব্যবসায়ীর বাড়িও উড়ে গিয়েছিল। দেখে মনে হচ্ছিল যেন কোনো শত্রুপক্ষের গোলায় একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে গোটা শহরটা।'
এই হল সাঁইতিরিশের তুফানের কাহিনী। স্মরণকালের সবচেয়ে বড় ঝড়গুলির অন্যতম ১৭৩৭-এর এই মহাঝঞ্ঝা।
 siki | 123.242.248.130 | ২৩ মার্চ ২০১১ ১৪:৫৭468862
siki | 123.242.248.130 | ২৩ মার্চ ২০১১ ১৪:৫৭468862- কলিকাতা সেকালে ও একালে বইতে মনে হয় এই বিবরণটা দেওয়া আছে।
 9 | 61.90.164.27 | ২৩ মার্চ ২০১১ ১৫:৫৬468863
9 | 61.90.164.27 | ২৩ মার্চ ২০১১ ১৫:৫৬468863- ১৭৩৭-এই কি ডিঙাভাঙার জন্ম, পরবর্তীকালের ক্রিক রো? হাতের কাছে রেফারেন্স নেই বলে মেলাতে পারছি না।
 nyara | 203.110.238.16 | ২৩ মার্চ ২০১১ ১৬:০১468864
nyara | 203.110.238.16 | ২৩ মার্চ ২০১১ ১৬:০১468864- আমার কাছেও রেফারেন্স নেই বলে চেক করতে পারছি না। এই ঝড়েই কি উল্টোডিঙির জন্ম - যেখানে একটা ডিঙি উড়ে এসে উল্টো হয়ে পড়ে ছিল?
 dri | 117.194.235.130 | ২৩ মার্চ ২০১১ ২২:৪৯468865
dri | 117.194.235.130 | ২৩ মার্চ ২০১১ ২২:৪৯468865- স্যার ফ্রান্সিস রাসেল কোন জন? একে তো খুঁজে পাচ্ছি না। অলিভার ক্রমওয়েলের এক প্রপৌত্র বার্টরান্ড রাসেলকে পেলাম।
আর গঙ্গার উজানে ৩০০ কিলোমিটার মানে কদ্দুর? কোলকাতা তো ছাড়িয়ে যাবে। নদীয়া?
 achintyarup | 121.241.214.38 | ২৪ মার্চ ২০১১ ০১:০০468867
achintyarup | 121.241.214.38 | ২৪ মার্চ ২০১১ ০১:০০468867- @ dri:
অলিভার ক্রমওয়েল সায়েবের নয়জন পুত্রকন্যা ছিলেন। একজন মারা যান শৈশবে। তাঁর নাম খুঁজে পাচ্ছি না। বাকিরা ছিলেন: রবার্ট, অলিভার, ব্রিজিত, রিচার্ড, হেনরি, এলিজাবেথ, জেমস, মেরি এবং ফ্রান্সেস।
ফ্রান্সেস জন্মেছিলেন ১৬৩৮ সালে। নাকি ক্রমওয়েলের সবচেয়ে প্রিয় সন্তান ছিলেন। আর্ল অব ওয়রউইকের নাতি রবার্ট রিচ-এর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয় ১৬৫৭ সালে। বিয়ের মাস তিনেকের মধ্যেই রিচবাবু বালতিতে লাথি মারেন। পরবর্তীকালে সার জন রাসেলকে বিয়ে করেন ফ্রান্সেস। দ্বিতীয় দাম্পত্য জীবন সুখে কাটিয়ে ১৭২১ সালে মারা যান ভদ্রমহিলা।
ফ্রান্সেস-এর এক পুত্রের নাম জন রাসেল। তিনি ১৭১১ থেকে ১৭১৩ পর্যন্ত কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ামের গভর্নর ছিলেন। এই জন সাহেবের পুত্রই ছিলেন সার ফ্রান্সিস রাসেল, যিনি ঐ ১৭৩৭-এর ঝড়ের বিবরণ লিখে গেছেন।
সার ফ্রান্সিস ছিলেন সিক্সথ ব্যারনেট অব শিপেনহ্যাম (চিপেনহ্যাম?), ইন দ্য কাউণ্টি অব কেম্ব্রিজ। ফোর্ট উইলিয়ামের কাউন্সিল সদস্য ছিলেন। ১৭৪৩ সালে কলকাতায় দেহ রাখেন।
ঐ ৩০০ কিলোমিটার (৬০ লীগ) দূরত্বের কথা লেখা ছিল জেণ্টলম্যান'স ম্যাগাজিনের রিপোর্টে। কতটা বিশ্বাসযোগ্য জানিনা।
 achintyarup | 59.93.241.155 | ২৪ মার্চ ২০১১ ০৪:০১468868
achintyarup | 59.93.241.155 | ২৪ মার্চ ২০১১ ০৪:০১468868- ও হরি! নয়জনের নামই তো এখেনে আছে গুণে দেখছি। কোনটে তাহলে ছোটবেলায় মারা গেল? যাগ্গে, পরে দেখব।
 achintyarup | 59.93.241.155 | ২৪ মার্চ ২০১১ ০৪:২৪468869
achintyarup | 59.93.241.155 | ২৪ মার্চ ২০১১ ০৪:২৪468869- ঝঞ্ঝার ঝঙ্কার : ১৮৬৪
""মাঠে মাঠে ধান পেকে পড়ে রয়েছে। গরু-ছগলে খেয়ে যাচ্ছে, তাড়া দিচ্ছে না কেউ। জিগ্যেস করলে বলছে, "কি হবে তাড়িয়ে? খাওয়ার মানুষ কোথায়?' '' -- ১৮৬৪ সালের ৭ই ডিসেম্বর তারিখের একটি চিঠিতে লিখেছেন মেদিনীপুর জেলার এক লাইটহাউসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। ঠিক দু মাস আগে ঝড় আর জলোচ্ছ্বাসে শূন্য হয়ে গেছে দক্ষিণ বাংলার গ্রামের পর গ্রাম। বাপ-মা-ভাই-বোন হারিয়ে যে কয়টা মানুষ বেঁচে আছে, সরকারি সাহায্যটুকু নেওয়ারও আর কোনো আগ্রহ নেই তাদের। দেখে অবাক হয়ে গেছেন অফিসাররা।
ঝড় এসেছিল ৫ই অক্টোবর। ঝড় আর জলোচ্ছ্বাস। বাংলার ছয়টি জেলার প্রায় পঞ্চাশ হাজার মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল মাত্র কয়েক ঘণ্টায়। ঝড়ের তীব্রতা ছিল প্রচণ্ড, কিন্তু সেই তুফানে যতটা প্রাণহানি হয়েছিল তার চেয়ে অনেক বেশি হয়েছিল জলোচ্ছ্বাসে। কিছু বোঝার আগেই পাড় উপচে ঢুকে আসা সাগরের হিংস্র জিভ টেনে নিয়েছিল হাজার হাজার মানুষকে।
সাত বছর আগে সিপাহী বিদ্রোহের যে ঝড় বয়ে গেছে সারা দেশের ওপর দিয়ে তার ক্ষত তখনও শুকোয়নি। এদিকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জায়গায় মহারাণীর শাসন চালু হয়েছে। রেলপথে অনেক কম সময়ে পৌঁছে যাওয়া যাচ্ছী দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। সংবাদ সংগ্রহ এবং সংরক্ষণের পদ্ধতি অনেক উন্নত এবং বিজ্ঞানসম্মত হয়েছে। ফলে বঙ্গোপসাগর থেকে ধেয়ে আসা সাইক্লোনে প্রতিটি জেলায় কতটা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তার মোটামুটি সত্যানুসারী বিবরণ লিপিবদ্ধ করে যেতে পেরেছেন রাজধানী শহর কলকাতার আবহাওয়াবিদরা।
সে সময়কার অনেক লেখাতেই ঝড়ের ইংরিজি নাম হারিকেনের বদলে সাইক্লোন লেখা হয়েছে। সাইক্লোন নামটি তখন নতুন। ঘূর্ণিঝড়ের এই নাম দিয়েছিলেন কলকাতার এক শিপিং ইন্সপেক্টর এবং শখের আবহাওয়াবিদ -- হেনরি পিডিংটন।
 achintyarup | 59.93.241.155 | ২৪ মার্চ ২০১১ ০৫:০৩468870
achintyarup | 59.93.241.155 | ২৪ মার্চ ২০১১ ০৫:০৩468870- এই পর্যন্ত এসে আর লোভ সামলাতে পারছি না। অমিতাভ ঘোষের হাংরি টাইড উপন্যাসের একটা অধ্যায় থেকে খানিকটা টুকে দিচ্ছি। অধ্যায়ের নাম আ পোস্ট অফিস অন সানডে -- রবিবারের ডাকঘর। এই অংশটা "আমার সময়'-এর পোবোন্ধে টুকিনি। (এই অংশে লেখা সবটুকুর সঙ্গে আমি একমত নই কিন্তু।)
""এই ভাটির দেশের অন্য আরও অনেক জায়গার মতই ক্যানিং-এর নামও দিয়েছিলেন একজন ইংরেজ সাহেব। সে সাহেব আবার যে সে সাহেব নন, একেবারে লাটসাহেব -- ভাইসরয় লর্ড ক্যানিং। এই লাটসাহেব আর তাঁর লেডি দেশ জুড়ে যেখানে সেখানে নিজেদের নাম ছড়িয়ে বেড়াতে ভালবাসতেন। তাঁদের পরবর্তী প্রজন্মের রাজনীতিকরা যেমন নিজেদের ছাই ছড়াতে পছন্দ করতেন, অনেকটা সেইরকম। অদ্ভুত অদ্ভুত সব জায়গার নাম আছে এই সাহেব-মেমের নামে -- রাস্তার নাম, জেলের নাম, পাগলা গারদের নাম। মজার ব্যাপারও অনেক হত। যেমন, লেডি ক্যানিং ছিলেন লম্বা, রোগা, একটু বদমেজাজি, কিন্তু কলকাতার এক মিঠাইওয়ালার মাথায় কী খেলল কে জানে, নতুন একটা মিষ্টি তৈরি করে তার নাম দিয়ে দিল মেমসাহেবের নামে। সে মিঠাই কিন্তু গোল, কালো আর রসে টইটম্বুর -- মানে লেডি ক্যানিং-এর চেহারা কি স্বভাব কোনওটার সঙ্গেই কোনও মিল নেই তার। তবুও কপাল খুলে গেল মিষ্টিওয়ালার। হু হু করে বিক্রি হতে লাগলা তার আবিষ্কৃত সেই নতুন মিঠাই। এত পরিমাণে লোকে সে মিষ্টি খেতে লাগল যে "লেডি ক্যানিং' -- এই পুরো কথাটা উচ্চারণ করতে যে সময় লাগে সে সময়টাও দিতে চাইল না তারা। মুখে মুখে মিষ্টিটার নাম হয়ে দাঁড়াল "লেডিগেনি'।
""এখন, লোকের মুখে ভাষা এবং শব্দের পরিবর্তনের নিশ্চয়ই নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম আছে। সেই নিয়মে যদি লেডি ক্যানিং হয়ে দাঁড়ায় লেডিগেনি, পোর্ট ক্যানিং-এর নামও তা হলে আস্তে আস্তে পালটে পোটুগেনি বা পোডগেনি হয়ে যাওয়া উচিত ছিল, তাই না? কিন্তু দেখ বন্ধুগণ, এই বন্দর শহরের নাম কিন্তু অপরিবর্তিত রয়ে গেল। এখনও মানুষ ঐ লাটসাহেবের নামেই চেনে ক্যানিংকে।
""কিন্তু কেন? কেন একজন লাটসাহেব তাঁর সুখের সিংহাসন ছেড়ে এই মাতলার কাদায় এসে নিজের নামের চাষ করতে গেলেন?
""মহম্মদ বিন তুঘলকের কথা মনে আছে তো তোমাদের? সেই পাগলা বাদশা, যিনি দিল্লি শহর ছেড়ে রাজধানি সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন এক অজ পাড়াগাঁয়? সেই একই ভূতে ধরেছিল বিলিতি সাহেবদেরও। একদিন হঠাৎ ওরা ঠিক করল নতুন একটা বন্দর চালু করতে হবে, বাংলাদেশের একটা নতুন রাজধানীর প্রয়োজন -- দ্রুত পলি জমছে কলকাতার হুগলি নদীতে, ওদের তাই মনে হল কলকাতা বন্দরের ডকগুলি আর কিছুদিনের মধ্যেই বুজে যাবে কাদায়। যথারীতি, সব প্ল্যানার আর সার্ভেয়াররা বেরিয়ে পড়ল দলে দলে, পরচুলা আর চাপা পাতলুন পরে চষে বেড়াতে লাগল সারা রাজ্যে, মাপজোক আর ম্যাপ তৈরি শুরু হয়ে গেল পুরোদমে। অবশেষে, এই মাতলার তীরে এসে একটা জায়গা পছন্দ হল ওদের। জেলেদের ছোট্ট একটা গ্রাম, তার সামনে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে নদী, আর সে নদী এমন চওড়া যে দেখলে মনে হয় সোজা সাগর পর্যন্ত বিছনো এক রাজপথ।''
 achintyarup | 59.93.241.155 | ২৪ মার্চ ২০১১ ০৫:২৬468871
achintyarup | 59.93.241.155 | ২৪ মার্চ ২০১১ ০৫:২৬468871- ""এখন, এটা তো সবাই জানে যে বাংলায় "মাতলা' কথাটার মানে হল "মত্ত'। আর এ নদীকে যারা চেনে তারা ভালই জানে কেন এর এই নাম। কিন্তু নাম আর শব্দ নিয়ে মাথা ঘামানোর এত সময় কোথায় সেই ইংরেজ টাউন প্ল্যানারদের? সোজা লাটসাহেবের কাছে ফিরে গিয়ে তাঁকে জানাল কী চমৎকার জায়গা একখানা খুঁজে পাওয়া গেছে। শোনাল কেমন বিশাল চওড়া আর গভীর নদী, সোজা গিয়ে মিশেছে সাগরে, তার পাশে কেমন সুন্দর টানা সমতল জায়গা; লাটসাহেবকে তাদের প্ল্যান আর ম্যাপ-ট্যাপ যা জা ছিল দেখাল, সেখানে কী কী বানানোর পরিকল্পনা আছে শোনাল তাঁকে -- হোটেল, বেড়ানোর জায়গা, পার্ক, বিরাট বিরাট প্রাসাদ, ব্যাঙ্ক, রাস্তাঘাট আরও কত কী। ও:, দারুণ সুন্দর একখানা শহর গড়া যাবে ঐ মাতলার তীরে -- কোনও কিছুর কোনও অভাব থাকবে না বাংলার সেই নতুন রাজধানীতে।
""ঠিকাদারদের ডেকে সব বুঝিয়ে-টুঝিয়ে দেওয়া হল, কাজও শুরু হয়ে গেল চটপট : হাজার হাজার মিস্ত্রি, মহাজন আর ওভারসিয়াররা এসে জড়ো হল মাতলার পাড়ে, শুরু করল খোঁড়াখুঁড়ি। মাতলার জল খেয়ে মাতালের মত কাজ করতে লাগল তারা, সব বাধা তুচ্ছ করে -- এমনকি ১৮৫৭-র বিদ্রোহের সময়ও বন্ধ হল না কাজ। তখন যদি এই মাতলার পাড়ে থাকতে বন্ধুগণ, তোমরা জানতেও পারতে না যে উত্তর ভারতে কেমন গ্রাম থেকে গ্রামে খবর চালাচালি হচ্ছে চাপাটির সঙ্গে, মঙ্গল পাণ্ডে কখন বন্দুক ঘুরিয়ে ধরেছে তার অফিসারদের দিকে, কাতারে কাতারে কোথায় খুন হয়ে যাচ্ছে নারী শিশু, কোথায় বিদ্রোহীদের উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে কামানের মুখে বেঁধে। এখানে প্রশান্ত নদীর পাড়ে কাজ চলতে লাগল অবিশ্রাম : বাঁধ তৈরি হল, ভিত খোঁড়া হল, নদীর ধার ঘেঁষে বানানো হল রাস্তা, বসানো হল রেলের লাইন। এবং এই পুরো সময়টা ধরে শান্ত ধীর গতিতে বয়ে চলল মাতলা, অপেক্ষা করে রইল। কিন্তু নদীও সব সময় তার সব গোপন কথা আড়াল করে রাখতে পারে না। এখানে যখন বন্দর তৈরির কাজ চলছিল, ঠিক সেই সময়ে কলকাতা শহরে বাস করতেন এক ভদ্রলোক, স্বভাব তাঁরও অনেকটা এই মাতলা নদীরই মত। সামান্য একটা শিপিং ইন্সপেক্টরের চাকরী করতেন তিনি -- ইংরেজ সাহেব, নাম হেনরি পিডিংটন। ভারতে আসার আগে এই পিডিংটন সাহেব কয়েক বছর কাটিয়েছিলেন ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে। সেখানকারই কোনও এক দ্বীপে থাকার সময় প্রেমে পড়েছিলেন সাহেব। না, কোনও মহিলাকে ভালবাসেননি ভদ্রলোক, এমনকী এরকম নির্জন জায়গায় বেশিদিন কাটালে অনেক সাহেব যেমন পাগলের মত তাদের কুকুরকে ভালবাসে, সেরকও কিছু ঘটেনি তাঁর জীবনে। মিস্টার পিডিংটন সেখানে ঝড়ের প্রেমে পড়েছিলেন। ঐ সব দ্বীপে সে ঝড়ের নাম ছিল হারিকেন, আর সেই হারিকেনকেই ভীষণ ভালবেসে ফেললেন সাহেব। অনেক লোক যেমন পাহাড় বা আকাশের তারা ভালবাসে, পিডিংটনের ভালবাসা কিন্তু ঠিক সেরকম ছিল না। ঝড় ছিল তাঁর কাছে বইয়ের মত, সংগীতের মত। প্রিয় লোক বা গায়কের প্রতি যেরকম একটা টান থাকে মানুষের, ক্যারিবিয়ানের তুফান ঠিক সেইভাবে টানত সাহেবকে। পিডিংটন ঝড়কে পড়তেন, শুনতেন, বুঝতে চেষ্টা করতেন, ঝড় নিয়ে চর্চা করতেন। ঝড়কে এত ভালবাসতেন উনি যে নতুন একটা নামই তৈরি করে ফেললেন -- "সাইক্লোন'।''
 achintyarup | 59.93.241.155 | ২৪ মার্চ ২০১১ ০৫:৪৬468872
achintyarup | 59.93.241.155 | ২৪ মার্চ ২০১১ ০৫:৪৬468872- ""এখন, আমাদের কলকাতা পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের মত অতটা রোমাণ্টিক জায়গা না হতে পারে, কিন্তু পিডিংটন সাহেবের প্রণয়চর্চার জন্য এ শহরও কোনও অংশে খারাপ ছিল না। ঝড়ের ভয়াল রূপের হিসাবে যদি বিচার করা যায়, দেখা যাবে বঙ্গোপসাগরের স্থান অন্য সব সমুদ্রের ওপরে -- সে ক্যারিবিয়ান সাগরই হোক, কি দক্ষিণ চীন সমুদ্র। আমাদের এই সাগরের তুফান থেকেই তো "টাইফুন' শব্দটা তৈরি হয়েছে, তাই না?
""লাটসাহেবের নতুন বন্দরের কথা একদিন কানে এল পিডিংটনের। ওঁর কিন্তু এতটুকু সময় লাগলা না বুঝতে যে কী মত্ততা লুকিয়ে আছে এই নদীর মধ্যে। এই মাতলার পাড়ে দাঁড়িয়ে তাকে উদ্দেশ্য করে সাহেব বললেন, "ঐ সার্ভেয়ারদের তুমি ফাঁকি দিতে পার, কিন্তু আমার সঙ্গে তোমার ওসব চালাকি খাটবে না। তোমার কি ধান্দা তা আমার জানতে কিছু বাকি নেই। বাকিরাও যাতে জানতে পারে সে ব্যবস্থা আমি শিগগিরই করছি।'
""মনে মনে হাসল মাতলা। বলল, "যাও না, এক্ষুণি যাও। বলো না গিয়ে। তোমাকেই সবাই বলবে মাতলা -- বলবে পাগল লোকটা নাকি নদী আর ঝড়ের মনের কথা পড়তে পারে!'
""কলকাতায় নিজের বাড়িতে বসে একের পর এক চিঠি লিখতে লাগলেন পিডিংটন। প্ল্যানারদের লিখলেন, সার্ভেয়ারদের লিখলেন -- কী বিপজ্জনক কাজ তারা করছে বললেন সে কথা; বললেন ভাটির দেশের এত গভীরে শহর গড়ার চিন্তা নিছক পাগলামি বই কিছু নয়; বাদাবন হল সাগরের সঙ্গে লড়ার জন্য বাংলার অস্ত্র, প্রক্রিতির প্রচণ্ড আক্রমন থেকে দক্ষিণ বাংলাকে আড়াল করে রাখে এই জঙ্গল; ঝড় ঢেউ আর জলোচ্ছ্বাসের প্রথম ঝাপটাটা এই সুন্দরবনই সামলায়। ভাটির দেশ যদি না থাকত কবে জলের তলায় চলে যেত বাংলার সমতলক্ষেত্র। এই বাদাবনই তো এতদিন বাঁচিয়ে রেখেছে পশ্চাৎভূমিকে। কলকাতার দীর্ঘ আঁকাবাঁকা সমুদ্রসড়ক আসলে হল সাগরের তুমুল শক্তির হাত থেকে বাঁচার জন্য প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। সেই তুলনায় তো এই নতুন বন্দর একেবারে অরক্ষিত। কখনো যদি সেরকম জোরালো স্রোত আর হাওয়ার টান ওঠে তাহলে সামান্য একটা ঝড়েই ভেসে যাবে গোটা জায়গাটা -- সাইক্লোনের টানে একটা ঢেউ ওঠার শুধু অপেক্ষা। মরিয়া হয়ে পিডিংটন ভাইসরয়কে পর্যন্ত লিখে ফেললেন একটা চিঠি : বিষয়টা আরেকবার ভাল করে ভেবে দেখতে অনুরোধ করলেন, ভবিষ্যদ্বাণীও করলেন -- বললেন সত্যি সত্যি যদি বন্দর তৈরি হয় এই জায়গায়, পনেরো বছরের বেশি সে বন্দর টিঁকবে না। একদিন আসবে, যখন প্রচণ্ড সাইক্লোনের সঙ্গে আছড়ে পড়বে লোনা জলের বিশাল ঢেউ, ডুবিয়ে দেবে গোটা বসতিটাকে; এর জন্য মানুষ হিসাবে এবং বৈজ্ঞানিক হিসাবে নিজের মানসম্মান পণ রাখতেও রাজি তিনি -- লিখলেন পিডিংটন।
 kumudini | 122.162.247.54 | ২৪ মার্চ ২০১১ ২২:৫৯468873
kumudini | 122.162.247.54 | ২৪ মার্চ ২০১১ ২২:৫৯468873- অচিন্ত্যরূপ,খুব ভালো লাগছে পড়তে।আজ লিখবে তো?
 dri | 117.194.232.176 | ২৫ মার্চ ২০১১ ০০:২৭468874
dri | 117.194.232.176 | ২৫ মার্চ ২০১১ ০০:২৭468874- সিক্সথ ব্যারনেট অফ শিপেনহ্যাম পাচ্ছি। কিন্তু উইকি এর সম্বন্ধে কোন ইনফোই পেলাম না। আর এই বিলিতিগুলোর নাম হয় জন, নয় ফ্রান্সিস। এত ফ্রান্সিস রাসেল যে গুলিয়ে যাচ্ছে। তবে স্ট্রেঞ্জ এই যে এই ফ্রান্সেস এবং জনের নাতি বার্ট্রান্ড রাসেলও। তার মানে এরা দুজন কাজিন হল। এদের সময়কালটা কিন্তু বেশ আলাদা। তবে বার্ট্রান্ড প্রায় ১০০ বছর বেঁচেছিলেন, সেটাও দেখতে হবে।
 I | 14.99.242.93 | ২৫ মার্চ ২০১১ ০০:৩৬468875
I | 14.99.242.93 | ২৫ মার্চ ২০১১ ০০:৩৬468875- অচিন্টি কাজ নিয়ে খুব প্যাশনেট আর পারফেকশনপ্রণয়ী। এইটা আমার বেশ ভাল্লাগে।
 NIna | 68.84.239.41 | ২৫ মার্চ ২০১১ ০৪:৩০468876
NIna | 68.84.239.41 | ২৫ মার্চ ২০১১ ০৪:৩০468876- চিন্টুবাবু, কি ভাল যে লাগছে ---জাদু কি ছড়ি আছে তোমার হাতে ---
 achintyarup | 59.93.240.149 | ২৫ মার্চ ২০১১ ০৪:৪২468878
achintyarup | 59.93.240.149 | ২৫ মার্চ ২০১১ ০৪:৪২468878- ""খ্যাপা সাহেবের এসব কথায় অবশ্য কেউই কান দিল না; প্ল্যানারদের বা লাটসাহেবের কারওরই এসব নিয়ে মাথা ঘামানোর মতো সময় ছিল না। কে পিডিংটন? সামান্য একটা শিপিং ইন্সপেক্টর বই তো কেউ নয়। সাহেবদের জাতপাতের হিসেবে একেবারে নিচের দিকে তার স্থান। লোকে ফিসফাস করতে শুরু করল -- আসলে মানুষটা একটু খ্যাপাটে তো, মাথায় অল্পবিস্তর গণ্ডগোল থাকাও বিচিত্র নয়। ও-ই তো কিছুদিন আগে বলেছিল না, যে ঝড় হল গিয়ে আসলে এক রকমের "আশ্চর্য ধূমকেতু'?
""সুতরাং কাজ চলতেই থাকল, বন্দরও তৈরি হয়ে গেল। বাঁধানো রাস্তাঘাট হল, রং-টং করা তকতকে সব হোটেল, ঘরবাড়ি হল, মোটকথা যেমন যেমন ভাবা হয়েছিল ঠিক সেইভাবে বানানো হল শহরটাকে। তারপরে একদিন খুব হৈ হল্লা করে ঢাকঢোল বাজিয়ে উৎসব হল, ভাইসরয় পা রাখলেন মাতলার পাড়ে, নতুন বন্দরের নাম দিলেন পোর্ট ক্যানিং।
""পিডিংটন সাহেবকে কিন্তু সে উৎসবে যোগ দিতে ডাকা হয়নি। কলকাতার রাস্তায় তাকে দেখা গেলেই এখন লোকজন হাসি তামাশা করে : ঐ যে, ঐ দেখ রে, মাতাল পিডিংটন বুড়ো যাচ্ছে। ঐ লোকটাই তো নতুন বন্দরের কাজ আটকানোর জন্য জ্বালিয়ে মারছিল লাটসাহেবকে। কী একটা যেন ভবিষ্যদ্বাণীও করেছিল না? আবার নাকি মানসম্মান পণ রেখেছিল নিজের?
""অপেক্ষা করো, অপেক্ষা করো, বললেন পিডিংটন -- পনেরো বছর সময় দিয়েছি আমি। মাতাল সাহেবের ওপর দয়া হল মাতলার। পনেরো বছর তো অনেক লম্বা সময়, এর মধ্যেই যথেষ্ট ভোগান্তি হয়েছে লোকটার। একটা বছর সাহেবকে অপেক্ষা করিয়ে রাখল মাতলা, তারপর আরও এক বছর, তারপর আরও এক। এই করে করে কেটে গেল পাঁচ পাঁচটা বছর। অবশেষে একদিন, ১৮৬৭ সালে, যেন শক্তিপরীক্ষার সমস্ত প্রস্তুতি নিয়ে ফুঁসে উঠল নদী। আছড়ে পড়ল ক্যানিং-এর ওপর। মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ভেসে গেল শহরটা -- কঙ্কালটুকু শুধু পড়ে রইল।
""বিশাল কোনও তুফান নয়, পিডিংটন ঠিক যেমনটি বলেছিলেন, সেইরকম সাধারণ একটা ঝড় উঠেছিল। সেই ঝড়ের হাওয়ায় নয়, তার সঙ্গে ওঠা একটা ঢেউয়ে -- একটা জলোচ্ছ্বাসে -- গুঁড়িয়ে গেল গোটা শহর। তার চার বছর পর, ১৮৭১ সালে, অবশেষে পরিত্যক্ত বলে ঘোষণা করা হল বন্দরটাকে। যে বন্দরের একদিন পুব সাগরের রাণী হয়ে ওঠার কথা ছিল, টক্কর দেওয়ার কথা ছিল বোম্বাই, সিঙ্গাপুর আর হংকং-এর সঙ্গে, সে এখন হয়ে গেল মাতলার কেনা বাঁদী -- ক্যানিং।''
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
-
গুরুচণ্ডা৯-র গ্রাহক হোন
কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে গুরুচণ্ডা৯-র গ্রাহক হোন। গুরুচণ্ডা৯তে প্রকাশিত লেখাগুলি পেতে চাইলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যুক্ত হোন, অথবা, আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলটির গ্রাহক হোন।
- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই
- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... মিঠু মণ্ডল )
(লিখছেন... Q, হেহে, রমিত চট্টোপাধ্যায়)
(লিখছেন... Amit Chatterjee, অমিতাভ চক্রবর্ত্তী, Amit)
(লিখছেন... দ, অমিতাভ চক্রবর্ত্তী, Kishore Ghosal)
(লিখছেন... Pk, অসিতবরণ বিশ্বাস )
- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন
(লিখছেন... Technical question, সমরেশ মুখার্জী)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... kk, অমিতাভ চক্রবর্ত্তী, সমরেশ মুখার্জী)
(লিখছেন... Aranya , হীরেন সিংহরায়, মোহাম্মদ কাজী মামুন)
(লিখছেন... অসিতবরণ বিশ্বাস )
- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... যোষিতা)
(লিখছেন... অরিন, অরিন, অমিতাভ চক্রবর্ত্তী)
(লিখছেন... সমরেশ মুখার্জী, ছোট মুখে , সমরেশ মুখার্জী)
(লিখছেন... পাপাঙ্গুল, দীপ, দীপ)
(লিখছেন... kk, দীপ, dc)
- কি, কেন, ইত্যাদি
- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...
- আমাদের কথা
- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...
- বুলবুলভাজা
- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...
- হরিদাস পালেরা
- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...
- টইপত্তর
- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...
- ভাটিয়া৯
- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...
- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।
গুরুচণ্ডা৯-র সম্পাদিত বিভাগের যে কোনো লেখা অথবা লেখার অংশবিশেষ অন্যত্র প্রকাশ করার আগে গুরুচণ্ডা৯-র লিখিত অনুমতি নেওয়া আবশ্যক।
অসম্পাদিত বিভাগের লেখা প্রকাশের সময় গুরুতে প্রকাশের উল্লেখ আমরা পারস্পরিক সৌজন্যের প্রকাশ হিসেবে অনুরোধ করি।
যোগাযোগ করুন, লেখা পাঠান এই ঠিকানায় : [email protected] ।
মে ১৩, ২০১৪ থেকে সাইটটি
বার পঠিত