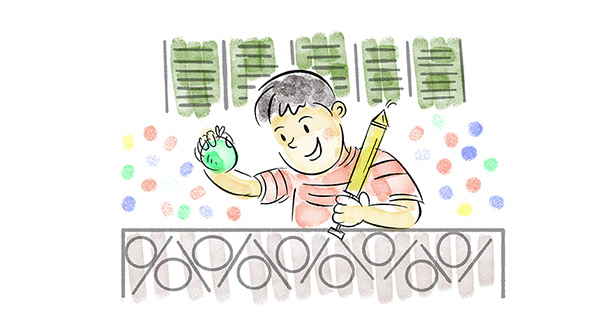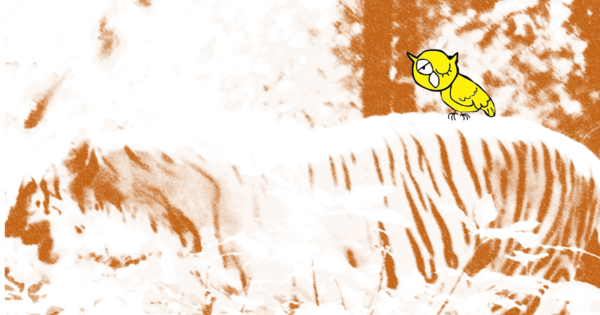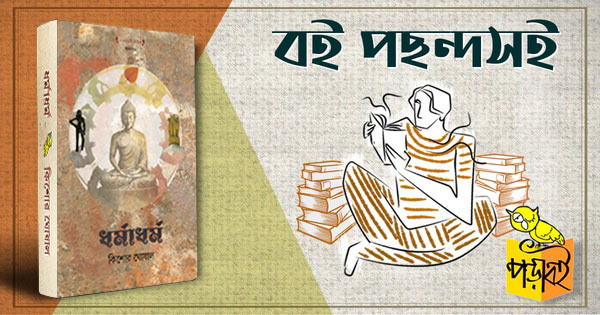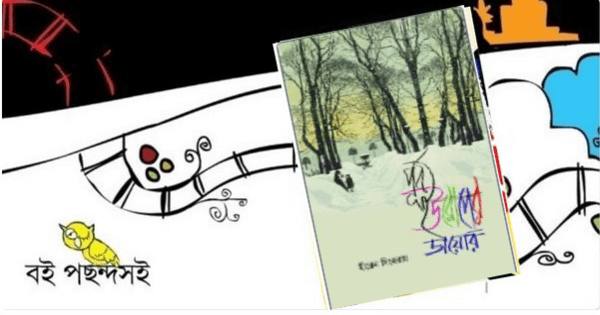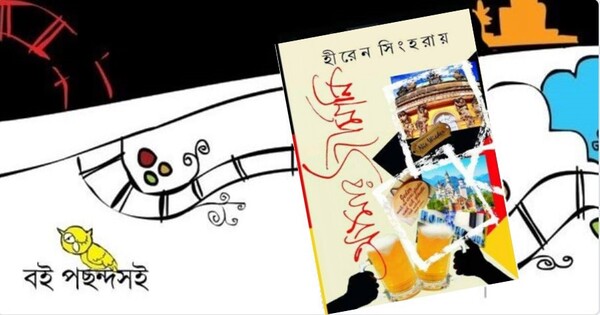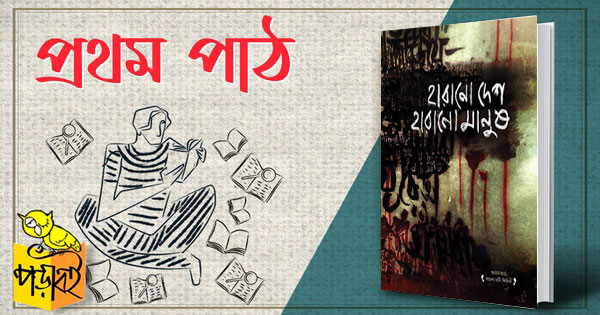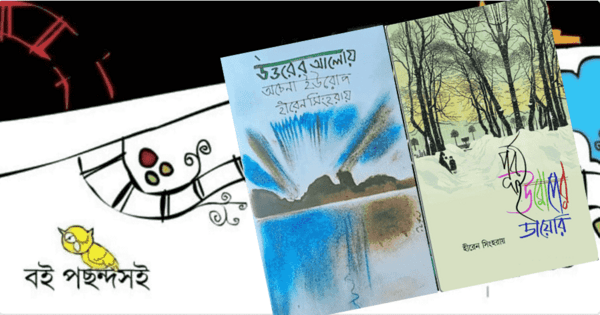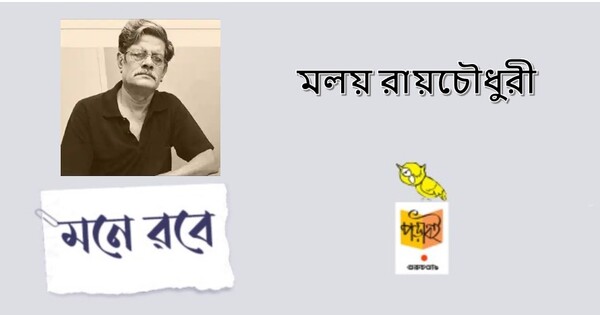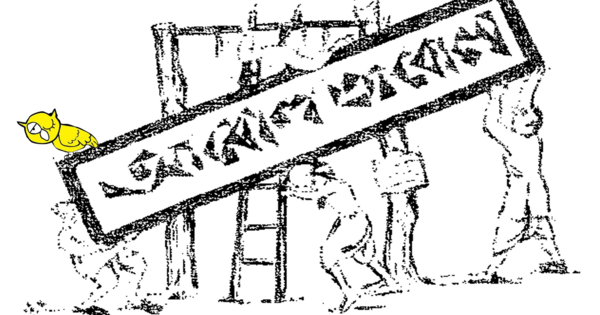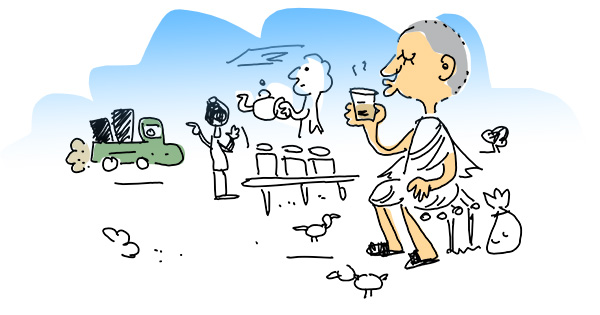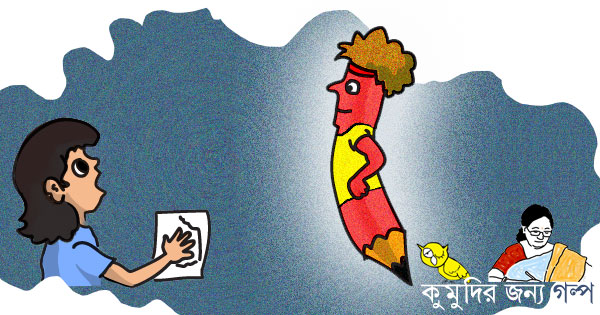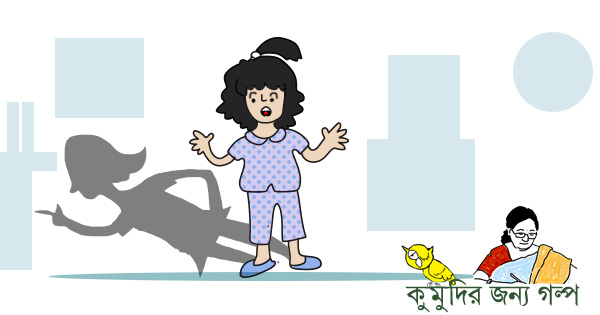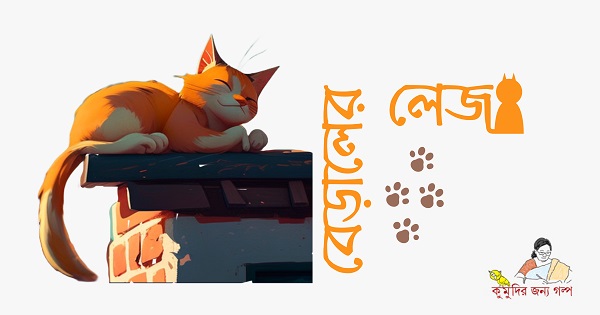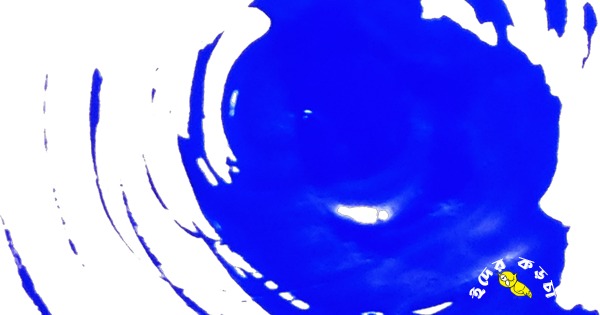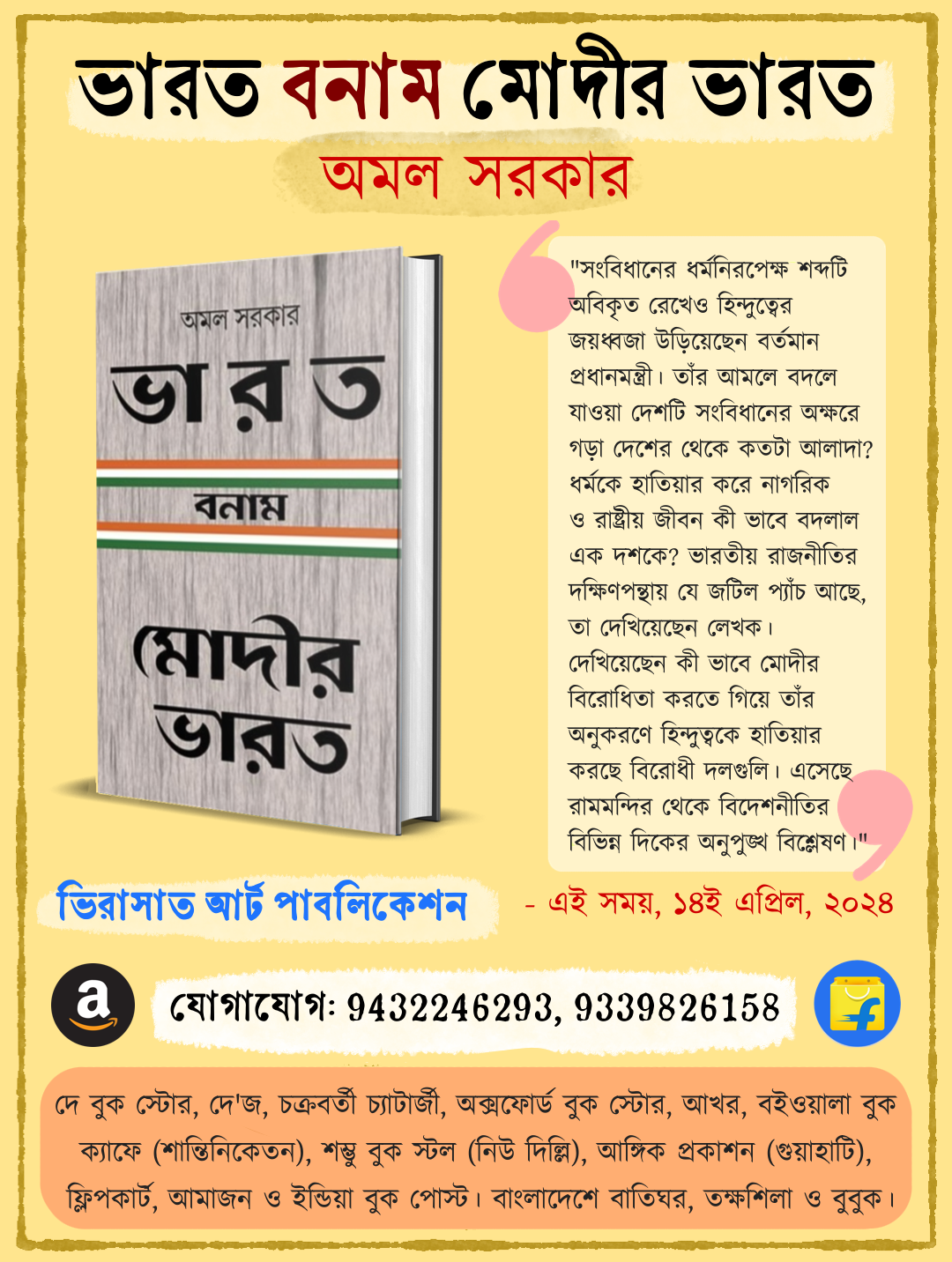তাজা বুলবুলভাজা...
দয়াময়ী-সন্ধেবেলা - জগন্নাথদেব মণ্ডল | সন্ধেবেলা দয়াময়ীর এই কথাটুকু মনে পড়ল দয়াময়ীর দয়াময়ী ছাড়া কেউ নেই। আজানে তখন আকাশ ফেটে গেছে, গলে গলে নামছে অন্ধকারের প্রথম দিককার রঙ। পেয়ারা ফুলের মতো মুখ নিয়ে ও কান পেতে শুনল সরসর করে কোথাও কিছু একটা বাজছে। বোঝা গেল, একেবারে একা একটা তালগাছ মাঠের মাঝখানে হাওয়ায় পাতাদের কাঁপাচ্ছে।ভাত খেতে বসে ওঁর বুক উদাস হয়, একজন কেউ থাকলে ভালো হত। এই এতবড়ো নীলসাদা রঙীন বাড়ি,দেওয়ালে সদ্য চুনকামের গন্ধ বুকে উঠে আসে। চিরকাল মাটির ঘরে, পাতার ঘরে দিন কেটেছে। সরকারি প্রকল্পের একা একা বিধবার মতো ফাঁকা বাড়িতে অস্বস্তি হয়, সন্ধ্যামালতী ফুলের চেয়েও নরম মা দেখে যেতে পারল না এই ঘরদোর।নিজেকে নিজের জল গড়িয়ে নিতে হলে, ভাতের পাতে কাঁচালঙ্কা-নুন বারবার আনতে যেতে হলে ভালো লাগে না। এতো যত্নে করা রান্নাবান্না অর্থহীন হয়ে পড়ে যতোক্ষণ না কেউ সেই খাবার খেয়ে একমুখ হাসিতে তারিফ করে ওঠে। চিংড়ি মাছের মাথার চচ্চড়ি তারিফ না করলেও মুখ তুলে অন্তত বলুক বিচ্ছিরি হয়েছে খেতে, এ রান্না খাওয়া যায় না। পরের দিন সে সব মায়ামমতা ঢেলে এমন মোচাঘন্ট রাঁধবে সেদ্ধ ছোলার তুক কাজে লাগিয়ে যে, কর্তাকে থালা অবধি চেটে খেতে হবে।বিয়ের বয়েস ঢিবি থেকে গড়াতে শুরু করেছে। সাতাশের কোঠায় বয়েস, শীর্ণ হাত দুটো, চোখে পশুপাখির মায়া মাখানো। কেউ না থাকার ছায়ামাখা বাড়িতে তপ্ত রোদে খালি পা ফেলে ফেলে অনেক সন্ন্যাসীরা আসবে আজ।সুতির শাড়ি গায়ে জড়িয়ে ভোরবেলা অনেক সময় নিয়ে চান করে সমস্ত শীতল ফলমূল কাটা সারা, গতরাতে ভেজানো আছে ছোলা ও মুগ , সকালে অঙ্কুরিত হবে, এবারে আমছেঁচাটা করে নিলেই হয়ে যাবে যোগাড়।ওদের পাড়ায় একেক দিন একেক বাড়ি ঘুরে ঘুরে গাজন সন্ন্যাসীরা সেবা নেয়। কতোজন আসবে বলা হয় না। আমবাগানের মাঝে যে ঠান্ডা জলের পুকুর সেখানে একেকজন সন্ন্যাসী স্নান শেষ করলেই ঢাক বেজে ওঠে।এভাবে ওই বাদ্য শুনে শুনে দেওয়ালে দাগ কেটে রাখতে হয়। চারজনের সোজা দাগ হয়ে গেলেই পাঁচ নম্বরে পেট বরাবর দাগ টেনে দিতে হয়, এভাবে অদ্ভূত আঁকচিত্রে বোঝা যায় কতোজন আসবে দুপুরে।পাথরের হামানদিস্তায় কাঁচা আম, গুড়ে কুটে তৈরি হল দেহ ঠান্ডা রাখার আমছেঁচা। সবাই আনন্দ করে খেল ফলমূল। জয় দিল শিবের নামে। তারপর ফিরে গেল চড়ক তলায়। পাড়ার বাচ্চারাও আঁজলায় প্রসাদ নিয়ে ফিরে গেছে, শুধু যায়নি রমা, পাশের বাড়িতে থাকে। বিষধুতুরা ফুলের মতো থুতনি, তুতলে তুতলে কথা বলে, মুখ দিয়ে লাল ঝরে। ভারি ন্যাওটা।- এ পিতি, মেলায় ককন যাবি? একনি আমায় নিয়ে চ।রমা বলে। দয়া ওর মাথার চুলে বিলি কেটে কিছু বলে না। - আমাল এট্টা বনদুক তাই, ঢিক ঢিক কলে থবাইকে মালব, এ পিতি। দয়া বলে - ঠিক আছে বিকেলে রোদ কমলে যাব, এখন বাড়ি যা।- আমাল ভূতের ভয় কলে বালি যেতে।- দিনেবেলা কীসের ভয় খেপি! ঠিক আছে দিয়ে আসি চ, বলে বাড়ির কাছাকাছি হাত ধরে দিয়ে আসে একরত্তি মেয়েটাকে।সারা উঠোন ছেয়ে আছে বয়স্ক পাতায়। পা ধোয়ানো একটু জলে কয়েকটা ছাপ। বাকি জল বসুমতী শোঁ করে পান করেছে।বাইরের দরজা ভেজিয়ে ও উঠোনে খুঁজতে লাগল খগেন দার পায়ের ছাপ। খগেন দা এখন সন্ন্যাসী সেজেছে। শ্যামলা ছিপছিপে চেহারা। দিনের অনেকভাগ সাইকেল চালিয়ে যায়। শহর থেকে একা গিয়ে পাইকারি রেটে মাল খরিদ করে আনে। বাজারে বসে ফল বিক্রি করে। ওর ভালোমানুষ বউ, প্রথম সন্তান নষ্ট হয়ে গেছে, দ্বিতীয়টা মেয়ে, রমার সঙ্গে খেলতে আসে মাঝে মাঝে উঠোনে, দেখলে দয়ার বুক টাটিয়ে ওঠে।খগেন চৈত্রমাসটা কামায়। আজ তরমুজের ফালি শালপাতার বাটিতে দিতে গিয়ে বয়স্ক চোখে দয়া দেখেছে ওর লোমহীন বগল, গভীর নাভি, খেটে খাওয়া শিরা ওঠা হাত। ওই হাত অল্প বয়সে জগদ্ধাত্রী পুজোর রাতে দয়াকে মধুর করেছিল।পুজোর রাত। চারিদিকে অল্প অল্প কুয়াশা। ইস্কুলের পাশে ছমছমে বারান্দায় ওকে শুইয়ে ঝাঁকড়া চুলো মাথাটা বুকে একবার রেখেছিল। খগেনের প্যান্ট তখন কিছুটা নেমে গেছে কোমর থেকে। সারা বুক, পেট ও পেটের নীচে ঘন চুলের দীর্ঘ বনজঙ্গল। সারা গা থেকে ঘুরে ঘুরে দিশি কমলালেবুর কাঁচা ও টক গন্ধ উঠছে। সেই কোন ছোট বয়সের ভয় ও অবশ ভালোলাগার স্মৃতি। ওইটুকু প্রথম পুরুষ স্পর্শ, ওইটুকুই শেষ।দয়াময়ী ছড়ানো ছিটানো কাজ সেরে আবার একবার চান করল। নিজের সেলাই করে জমানো টাকা, মায়ের বিধবা ভাতার পুরোনো টাকা গুনেগেঁথে ফলাহার করে বিছানায় একটু গড়িয়ে নিতে গিয়ে বেলা পড়ে গেল। মাথার কাছে অন্ধকার। রমা ডেকে ফিরে গেছে, মেলা থেকে কেনা লাল আইসক্রিম, পাঁপড়ভাজা দিয়ে গেল মায়ের সঙ্গে এসে।ভালো করে সন্ধে হয়েছে। আজ আবার রাঁধতে ইচ্ছে করছে না। মাথাটা ধরে আছে। দুয়োর বন্ধ করতে করতে দয়াময়ীর আবার মনে পড়ল দয়াময়ীর দয়াময়ী ছাড়া আর কেউ নেই।অবেলায় কিন্তু শোয় না দয়া। আজ শুয়ে ঠান্ডা আইসক্রিম টা মুখে নিল। শরীরে শিহরণ হল। মুখ থেকে বের করে বুক উদলা করে নালঝোল মাখা আইসক্রিম চোখ বন্ধ করে বুকে রাখল। আবার মুখে নিল। বুনো ফলের উগ্র গন্ধ। শরীর শিরশির করছে। লাল রঙের দশটাকা দামের সস্তা আইসক্রিম ওঁকে সুখ দিচ্ছে। এইবার দুই বৃন্তে রঙীন বরফ চেপে ঘোরাতে লাগল চির-আইবুড়ো মেয়ে। দয়ার চোখ জল। শরীর-বিছানা ভিজে গেছে ও ভেসে গেছে। বুকে একটি চ্যাপ্টা রঙের কাঠি পড়ে আছে। কাঠিটা রমার মতো পাতলা। বুক স্নেহে ব্যথা করে।কাঠিটাকে ছুঁয়ে দয়াময়ী ফিসফিস করে বলে-খোকা, তোর মা মরে গেলে মুখে আগুন দিস, আমগাছটা বিক্রি করে গয়ায় পিণ্ডিদান করিস, ভূত হয়ে ঘুরে বেড়ানোর কষ্ট আমি বইব না রে। এই একা একা বেঁচে থাকার দুঃখ আবার মরে গেলেও একলার কষ্ট আমার আর সইবে না রে।এরপর দয়া শুয়ে শুয়ে কেমন করে যেন গুমরে গুমরে হাসে। দক্ষিণ দিক থেকে গাছের বাজনা শোনা যায়। সাপ বেরিয়েছে গর্ত থেকে গায়ে বাতাস লাগাতে। অনেক রাত হয়ে গেছে।ভক্স পপুলি - যদুবাবু | “In general, a law which has not been voted unanimously involves subjecting men to an opinion which is not their own, or to a decision they believe contrary to their interest. It follows that a very great probability of the truth of this decision is the only reasonable and just grounds according to which one can demand such submission.” - Marie-Jean-Antoine-Nicolas de Caritat, Marquis de Condorcet (September 17, 1743–March 28, 1794)এই লেখাটা যখন লিখছি, অর্থাৎ এই ২০২৪-এর এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে, আমাদের চারদিকে ভোটের দামামা বেজে গেছে। সামাজিক মাধ্যম থেকে শুরু করে সমস্তরকম খবরের চ্যানেল ভরে গেছে ভোট-সংক্রান্ত খবরে, হয় দলবদলের অলীক কুনাট্যরঙ্গ, না হলে অপদার্থ রাজনীতি-ব্যাবসায়ীদের তামাশা, অথবা কাদা-ছোঁড়াছুঁড়ির মহড়া। ভোট যত এগিয়ে আসবে, নিউজ়-ফিড ভরে যাবে বিচিত্র-বিবিধ সব “ফলিবেই ফলিবে” গোছের ভবিষ্যদ্বাণীতে, আর সেই নিয়ে নিত্যি তুফান উঠবে চায়ের কাপে আর আড্ডায়-তর্কে।ভোটের ফলের পূর্বাভাস অথবা প্রেডিকশন কিন্তু সেই সমস্ত জটিল ধাঁধার মত—পরীক্ষায় যেসব প্রশ্নের উত্তর মাথা খাটিয়ে হোক কিংবা হল-কালেক্ট করে বা স্রেফ আন্দাজে ঢিল মেরে একবার মিলিয়ে দিতে পারেন, কেউ খুব বেশি মাথা ঘামাবে না ঠিক কেমন করে, কোন মেথডে মিলিয়েছেন। আমাদের ভাষায়, ইন্টারপ্রিটেবিলিটির (“কী করে?”) চাইতে অ্যাকিউরেসির (“কতটা মিলেছে”) দর ও কদর অনেক বেশি। আবার এও ঠিক, যে এই প্রতিযোগিতার পুরস্কার-তিরস্কার দুইই একটু বেশির দিকে। মিলিয়ে দিতে পারলে রাতারাতি সেলিব্রিটি, সবাই এসে থানে গড় করবে—যেমনটা হয়েছে বাবু নেট সিলভারের বেলায়—আর ফস্কে গেলে পাড়ার লোকে এসে বলে যাবে ‘সব ঢপ!’ সেই সঙ্গে, শুধু আপনার না, আপনার গোটা ফিল্ডের পাৎলুন ধরে টানামানি ব্যাপার।সে যাই হোক, আপনাদের যদুবাবু সেফোলজিস্ট নন, রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ অর্থাৎ পোলিটিক্যাল পানডিট (পন্ডিত) – সেও নন। তবে নেট সিলভারের নামে ধন্যধন্য হয়েছিল যে বছর, যদুবাবুও সেই সময় কিঞ্চিৎ গৌরবে বহুবচ্চন হননি এ কথা বললে ডাহা মিথ্যে বলা হবে। তবে, আজ সে সব না। আজকে প্রেডিকশনের ধারকাছ দিয়েও যাবো না আমরা। বরং আমরা উত্তর খুঁজবো আরও গভীর, কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে অতিসাধারণ একটি প্রশ্নের – গণতন্ত্র যে নির্বাচনের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে, সেই জনমত কি সবসময়েই অভ্রান্ত? Is the vox populi always correct? সহজ করে বললে, একদল মানুষ অর্থাৎ ভোটদাতা কি সংখ্যাগরিষ্ঠতার মাধ্যমে সবসময়েই ঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেন? আরেকভাবে বললে, যে মেজরিটি ভোটিং-এর উপর আমাদের গণতান্ত্রিক কাঠামোটিই দাঁড়িয়ে, সেই মেজরিটি কি সবসময়েই একটি অবজেক্টিভ (অর্থাৎ নৈর্ব্যক্তিক) সত্যতে পৌঁছুতে পারে? যদি পারে, তাহলে কখন পারে? আর যদি না পারে, তাহলে ঠিক কেমন ব্যাপার হয় সেটা? সামান্য এদিক-ওদিক দিয়ে কান ঘেঁষে না একেবারে বিচ্ছিরিভাবে ভুল? (এখানে ধরে নেওয়াই হচ্ছে যে একটি অবজেক্টিভ (অর্থাৎ বস্তুনিষ্ঠ বা নৈর্ব্যক্তিক) সত্যি আছে, অথবা, নির্বাচনের দিক থেকে ভাবলে সবার জন্যই (তর্কাতীতভাবে) মঙ্গলদায়ক এমন নীতি আছে।এই যে সকলে মিলে ঠিক উত্তরে বা ঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর ফেনোমেনন বা ঘটনা, এর-ই পোশাকি নাম “উইজ়ডম অফ ক্রাউড”, বাংলায় “সমষ্টিগত প্রজ্ঞা”। দর্শনে বা বিজ্ঞানের ইতিহাসে উইজ়ডম অফ ক্রাউডকে ব্যাখ্যা করার অথবা সংজ্ঞায় বা সূত্রে ধরার চেষ্টা বহুদিনের। আরও বহু জিনিসের মতোই, এর-ও সুতো ধরে টানতে টানতে পৌঁছে যাই সেই প্রাচীনকালের দার্শনিক অ্যারিস্টোটলের কাছে। ইনফর্মেশন এগ্রিগেশনের, বা তথ্য একত্র করার উপযোগিতার কথা সেই যুগে যারা ভাবতেন, তাঁদের মধ্যে সম্ভবত উনিই প্রথম। তবে, রাশিবিজ্ঞানের ছাত্রের কাছে “উইজ়ডম অফ ক্রাউডের” অতিপরিচিত গল্প অবশ্যই স্যার ফ্রান্সিস গ্যালটনের সেই বিখ্যাত এক্সপেরিমেন্ট, যেটি ছাপা হয়েছিল নেচার পত্রিকার মার্চ ১৯৪৯ সালের একটি নিবন্ধে, শিরোনাম “ভক্স পপুলি”। কীরকম ছিল সেই এক্সপেরিমেন্ট? গ্যালটন বর্ণনা দিয়েছেন প্লাইমাউথের একটি মেলার। সেখানে গেলে দেখা যেত একটি হৃষ্টপুষ্ট দুর্ভাগা ষাঁড় (ফ্যাটেনড অক্স) দাঁড়িয়ে আছে মেলার ঠিক মধ্যিখানে। দাঁড়িয়ে থাকার উদ্দেশ্য দর্শকদের মধ্যে একটি প্রতিযোগিতা – এই ষাঁড়টিকে কেটেকুটে পরিষ্কার করার পর সেই মাংসের ওজন কত হবে আন্দাজ করার। প্রতিযোগিতার প্রবেশমূল্য ধার্য করা হল ছয় পেনি, আর সবথেকে কাছাকাছি উত্তরের জন্য একটি পুরস্কার। গ্যালটন লিখছেন, ঐ ছয় পেনি মূল্যের উদ্দেশ্য—যাতে কেউ ইয়ার্কি মেরে ভুলভাল আন্দাজ না করেন (‘prevent from practical joking’), আর পুরস্কার পাওয়ার আশায় যারা আন্দাজ করছেন, তাঁরাও যথাসম্ভব সেরা আন্দাজ-ই করবেন (‘put the best bet’)। আর লিখেছেন, প্রতিযোগীদের বেশিরভাগ হয় চাষি, না হলে পশুপালক বা কসাই – কাজেই একেবারেই অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়ার মত ব্যাপার নয়। ফল কী হল? গ্যালটনের পেপারে পাই, সেইদিনের ৮০০খানা উত্তরের মধ্যে ১৩টি অসম্পূর্ণ উত্তর বাদ দিয়ে যা পড়ে থাকে, তার মধ্যমা (মিডিয়ান) নিলে দাঁড়ায় ১২০৮ পাউন্ড, আসল ওজন—১১৯৭ পাউণ্ডের—এক শতাংশের মধ্যেই, আর গড় (অর্থাৎ মিন) নিলে উত্তর একেবারেই মিলে যাচ্ছে খাপে-খাপ, যাকে বলে নিখুঁত লক্ষ্যভেদ [Wallis, 2014]। উপসংহারে গ্যালটন মন্তব্য করছেন, “This result is, I think, more creditable to the trustworthiness of a democratic judgment than might have been expected.” …শুধু আন্দাজ-মেলানো বা খেলা নয়, সমষ্টিগত প্রজ্ঞার বিভিন্ন ও বিচিত্র উদাহরণ কিন্তু দেখা যায় আমাদের প্রায় সমস্ত উদ্যোগেই, যেখানেই সিদ্ধান্ত নেওয়া (ডিসিশন-মেকিং) আর কিঞ্চিৎ অনিশ্চয়তা (আনসার্টনটি) মিশে আছে এমন সব ক্ষেত্রেই। যদি সত্য ধ্রুবক হয়, আর সমস্ত ভ্রান্তি যদ্দৃচ্ছ, অর্থাৎ এক-একটি ভুল এক-একদিকে টানছে (অর্থাৎ এররগুলো র্যান্ডম, সিস্টেমিক নয়), তাহলে গড় নিলে সেই সব ভুলগুলি কাটাকুটি করে ফলাফলের খুঁতশূন্যতা বা অ্যাকিউরেসি বাড়তে বাধ্য। এই নিয়ে ব্যাপক আলোচনার জন্য পাঠকদের “The Wisdom of the Crowds” [Surowiecki, 2005] বইটি সুপারিশ করে যাই।কিন্তু আজকের গল্প আরও পুরোনো – এরও প্রায় দেড়শো বছর আগের ফ্রান্স যার পটভূমি। ইতিহাস বলে উইজ়ডম অফ ক্রাউডের প্রথম যথাযথ অঙ্কের সূত্র এসেছিল সেই ‘এজ অফ এনলাইটেনমেন্টের’ সময়, ফরাসি বিপ্লবের ঢেউ আছড়ে পড়ার অব্যবহিত আগে। সেই গল্পের নায়ক কনডরসে, পুরো নাম Marie Jean Antoine Nicolas de Caritat, Marquis de Condorcet! কনডরসে-কে বলা হয় “দি লাস্ট অফ দ্য ফিলোজ়ফস”, সেই “আলোকিত যুগের শেষ সাক্ষী” – ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাসের একজন অতিমানবিক এবং অবশ্যই ট্র্যাজিক হিরো। তার গপ্পো করতে গেলে গোটা একটা বই-ই লিখে ফেলা যায়, তবু ছোট্ট করে বলি। কনডরসে মানবাধিকার ও সাম্যবাদে বিশ্বাস করতেন – সাম্যবাদ শুধু সব বর্ণের মধ্যেই নয়, সমস্ত অর্থনৈতিক শ্রেণির, এবং পুরুষ ও নারীর মধ্যেও। স্বল্প জীবনকালেই তিনি ওকালতি করেছিলেন শিক্ষাগত সংস্কার, প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার, ঔপনিবেশিক দাসত্বের বিলুপ্তি এবং নারীর সমানাধিকার, বিশেষ করে সব জাতির সমতার জন্য এবং নারীদের ভোটাধিকার (উইমেন্স’ সাফ্রেজ) প্রশ্নের। এবং এই শেষতম প্রশ্নে, কনডরসে সেই আলোকিত যুগেও যেন উজ্জ্বল ব্যতিক্রম [Landes, 2009]। শেষ জীবনে, সেই কুখ্যাত রেইন অফ টেররের রোবস্পিয়েরের ভয়ে আত্মগোপন করা অবস্থাতেও তিনি লিখে চলেছেন তার সেরা কাজ Esquisse — লিখছেন সমাজের অগ্রগতির (“উন্নয়ন” বা “বিকাশ” আজকাল ব্যাঙ্গাত্মক শোনায়) কাঠামো, যার মূল স্তম্ভ মানুষের অসীম পরিপূর্ণতা (indefinite perfectibility of humankind and society)। কনডরসে-র আরও এক অন্যতম অবদান, “সোশ্যাল অ্যারিথমেটিক” – আজকে দাঁড়িয়ে মনে হয় সমাজের বিভিন্ন জটিল সমস্যায়, আর্থিক পরিকল্পনা থেকে জুরি-র সিদ্ধান্ত গ্রহণ, অথবা জনস্বাস্থ্য, সর্বব্যাপী রাশিবিজ্ঞান বা সম্ভাব্যতা-তত্ত্বের প্রয়োগের এক্কেবারে শুরুর দিকে চিন্তক ও দার্শনিক উনিই।উইজ়ডম অফ ক্রাউডের গল্পে ফিরে আসি আবার। গ্যালটনের ১৬৪ বছর আগে, এই কনডরসে-ই, প্রথম অঙ্কের সূত্রে বেঁধেছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠের ব্যবহার – সমষ্টিগত প্রজ্ঞা অথবা মূর্খামি, দুইই। সেই বিখ্যাত উপপাদ্যটিই আজকে পরিচিত কনডরসে জুরি থিওরেম নামে, সংক্ষেপে CJT [Condorcet, 1785]। সেই উপপাদ্যটিই এখানে ছোট্ট করে, এবং সহজতম ভার্সনটিই, লেখার চেষ্টা করি। এই নিয়েও অবশ্য আস্ত বই আছে - Goodin and Spiekermann [2018], যদি পাঠকদের কারুর বিশদে পড়তে ইচ্ছে করে।আবারও, ধরে নেওয়া যাক একটি অবজেক্টিভ অর্থাৎ বস্তুনিষ্ঠ সত্যি বা সেরা বিকল্প আছে, সেটা কী—না জানলেও চলবে, কিন্তু সে আছে, সেইটির জন্যেই ভোটাভুটি হচ্ছে। আর ধরা যাক আমাদের n-সংখ্যক ভোটার আছে, n বিজোড় সংখ্যা (অর্থাৎ “টাই” অসম্ভব)। প্রত্যেক ভোটারের ঠিক বিকল্পে ভোট দেওয়ার সম্ভাবনা ধরা যাক pc, এবং সবার ভোট পড়ে গেলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে “মেজরিটি রুল” অনুযায়ী, অর্থাৎ যে সবথেকে বেশি ভোট পাবেন, সেটিই আমাদের গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত। কনডরসে-র উপপাদ্যে এও ধরে নেওয়া হয়, যে, প্রত্যেক ভোটার ‘স্বতন্ত্র’, ‘দক্ষ’ এবং ‘আন্তরিক’। ‘স্বতন্ত্র’ – অর্থাৎ যে যার নিজের ভোট দিচ্ছেন বা একজনের পছন্দ আরেকজনকে প্রভাবিত করে না। ‘দক্ষ’ – অর্থাৎ, প্রত্যেকের ঠিক বিকল্প খুঁজে নেওয়ার সম্ভাবনা অর্ধেকের থেকে বেশি, যত সামান্যই হোক, এক্কেবারে র্যান্ডম গ্যেস অর্থাৎ ইকির-মিকির-চামচিকির করে আন্দাজে যা-ইচ্ছে-তাই একটা বোতাম টিপে দেওয়ার থেকে তার প্রজ্ঞা বা দক্ষতা একচুল হলেও বেশি। আর শেষ অ্যাজ়াম্পশনের কথা আগেও লিখেছি, ভোটার-রা ‘আন্তরিক’, সিরিয়াস-ও বলা যায়—কেউ ইচ্ছে করে ভুলভাল ভোট দিয়ে নষ্ট করছেন না।কনডরসে-র উপপাদ্য বলে, এই সমস্ত অ্যাজ়াম্পশন সত্যি হলে, দুটো জিনিস হবেই – প্রথমত, মেজরিটি ভোটিং-এর মাধ্যমে ঠিক বিকল্প খুঁজে নেওয়ার সম্ভাব্যতা যেকোনো একজন ভোটারের ঐ এক-ই সম্ভাব্যতার থেকে বেশি হবে, আর যত ভোটারের সংখ্যা বাড়বে, ততই ঐ ঠিক উত্তরে পৌঁছনোর সম্ভাব্যতা ১-এর কাছাকাছি (অর্থাৎ ১০০%-এর কাছাকাছি) পৌঁছবে। সোজা বাংলায়, প্রচুর প্রচুর লোকে ভোট দিলে একেবারে ঠিক উত্তরে বা সেরা বিকল্পে পৌঁছনোর গ্যারান্টি দিচ্ছে CJT!অঙ্কের ফর্মুলা এই নিবন্ধে না দিলেও চলে, এবং ইচ্ছে করলেই এই সূত্রটি সোজা টপকে পরের প্যারায় লাফিয়ে চলে যেতেই পারেন, তবে এত সুন্দর ফর্মুলা, যে না দিয়ে থাকতে পারছি না। CJT বলছে, যদি মেজরিটি ভোটিং-এর সিদ্ধান্ত “ঠিক” হওয়ার সম্ভাব্যতা হয় Pn আর এক-একজন ভোটারের “ঠিক” ভোট দেওয়ার সম্ভাব্যতা হয় pc, তাহলে অল্প অঙ্ক করলেই যে সূত্রটি পাওয়া যায় সেটা এইরকম: অর্থাৎ, CJT বলছে pc >1/2 হলে, অর্থাৎ দক্ষ ভোটার হলেই,১) Pn+2 > Pn (মানে একজনের থেকে তিনজনের গড় নিলে ঠিক উত্তরে পৌঁছনোর সম্ভাবনা বেশি) আর২) Pn → 1 as n → ∞ (মানে যত বেশি দক্ষ ভোটার ভোট দেবেন, তত ১-এর দিকে ক্রমাগত এগিয়ে যাব, নিচের ছবির উপরের ভাগে যেমন দেখা যাচ্ছে।) বলাই বাহুল্য, যে এইটি একটু থেঁতো করে লেখা। এই উপপাদ্য একটু এদিক-ওদিক করলেও টেঁকে, যেমন সবার ঠিক উত্তর দেওয়ার সম্ভাবনা সমান নয়, না হলেও চলে, প্রত্যেকের সম্ভাবনা “আধা সে জ্যায়াদা” হলেই কেল্লা ফতেহ। আরো কিছু খোল ও নলচে পাল্টানো যায়, তবে কিনা, সে রাস্তায় আমরা আজকে যাবো না।এই আশ্চর্য সুন্দর অথচ সহজ আবিষ্কারটি কিন্তু বহুদিন হারিয়ে গেছিল ইতিহাসের গর্ভে। তাকে খুঁজে পাওয়া যায় দীর্ঘ সময় পরে, ডানকান ব্ল্যাক ও অন্যান্যদের ১৯৫৮ সালের একটি গবেষণাপত্রে। শুধু জুরি থিওরেম-ই নয়, কনডরসে-র বিখ্যাত ভোটিং প্যারাডক্সটিও। সেটা আবার আরেক আশ্চর্য জিনিস – ধরা যাক তিনটে পার্টি আছে, ক, খ আর গ। তাহলে, মেজরিটি ভোটিং-এর ফলে এমন হতেই পারে, যে মানুষ ক-র থেকে বেশি পছন্দ করে খ-কে, আবার খয়ের থেকে বেশি গ-কে, অর্থাৎ গ > খ, এবং খ > ক, কিন্তু অঙ্কের মত এর মানেই গ > ক ভোট পাবে তার গ্রান্টি নেই, সবাই ভোট দেওয়ার পর হয়তো দেখা গেল ক, গ-কে হারিয়ে দিয়েছে। খটোমটো করে বললে, ব্যক্তিবিশেষের পছন্দ চক্রাকার নয়।এই যেমন নিচের টেবিলটি দেখুন, আপনি যদি বলেন “গ”-ই সেরা, তক্ষুণি রাম আর শ্যাম বলবে – কেন, আমরা তো “গ”-এর থেকে “খ”-কে বেশি ভালোবাসি। আবার যেই বললেন – ঠিক আছে, তাহলে “খ”-কে জয়ী ঘোষণা করে দাও, তখন রাম আর মধু বলবে – সে কী! আমাদের চোখে তো “ক” অবশ্যই “খ”-এর থেকে ভালো। তাহলে কি “ক”-ই প্রধান-সেবক? নাঃ, শ্যাম আর মধু বলছে তাদের চোখে “গ”>”ক”! এ তো মহা মুশকিল! (উপরের টেবিলে যদু কেন মিসিং সে প্রশ্ন প্লিজ করবেন না।)এই ধাঁধার জট ছাড়াতেও আরেকটা গোটা লেখা দরকার, তবে কিনা, এই ছোট্ট ধাঁধার মধ্যেই লুকিয়ে আছে নোবেলজয়ী অ্যারো’জ় ইম্পসিবিলিটি থিওরেমের মূল সুর। যার মোদ্দা কথা – যে একদম সুষ্ঠুতম (ফেয়ারেস্ট) ভোটাভুটি হলেও এতোল-বেতোল লোকে জিতে যেতে পারে, মানে যাকে বলে ডেমোক্রেসির ফুটুরে একাধিক ডুমাডুম, অবশ্যই কিছু কিছু শর্ত সাপেক্ষে।আবার লাইনে ফিরে আসি। এই যে উইজ়ডম অফ ক্রাউডের গপ্পো করে যাচ্ছি, এর প্রভাব বলুন বা প্রয়োগ – তা কিন্তু শুদ্ধু ভোটাভুটির ফলেই নয়, আরও অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়। যেমন, আমাদের এই মেশিন লার্নিং-এর লাইনের আনসাম্বল লার্নার, উদাহরণ র্যান্ডম ফরেস্ট, যার আসল কথা এই, যে অনেকগুলো মডেলের প্রেডিকশন নিয়ে গড় করলে অ্যাকিউরেসি হু-হু করে বেড়ে যায়, যদি সেই মডেলগুলোর প্রত্যেকে মোটামুটি কিছুটা স্বতন্ত্র (“কিছুটা” মানে আমাদের লবজ়ে একেবারে ইন্ডিপেন্ডেন্ট না হলেও ডি-কোরিলেটেড, হুবহু টুকলি নয়), আর ‘দক্ষ’ হয় (প্রত্যেকেটা মডেল-ই আন্দাজে ঢিল মারার থেকে ভালো।)আরো একটা অঙ্কের ফর্মুলা দিয়ে যাই, এ-ও স্বচ্ছন্দে রাস্তায় জমে থাকা জলের মত ডিঙিয়ে যেতে পারেন, ক্ষতি নেই। এটা রোমান ভার্শিনিনের বইয়ের অঙ্ক। (রাশিবিজ্ঞানের ছাত্র হলে প্রমাণ করার চেষ্টা করতেই পারো, দুই লাইনের প্রুফ।)Consider a randomized algorithm for decision-making (e.g., determining if a number is prime) that gives correct answers with probability 1/2 + δ, where δ > 0 (i.e., assuming ‘competence’). By running the algorithm n times and taking the majority vote, the probability of obtaining the correct answer would be at least 1 − ε for any ε > 0, as long as, এ তো গেল সব ভালো ভালো কথা, “আমরা চলব আপন মতে, শেষে মিলব তাঁরি পথে” বলে কোরাসে গান গাওয়ার মত জায়গায় পৌঁছে গেছি প্রায়। কিন্তু তাহলে এই যে চাদ্দিকে বিভিন্ন সব অদ্ভুত ঘটনা দেখি – এই যেমন ব্রেক্সিট দেখলাম, ট্রাম্প-ও দেখলাম, আর আমাগো দ্যাশে তো আর কথাই নেই। এরা তো মেজরিটির-ই পছন্দ, তাহলে কোথায় গেলো সেই উইজ়ডম? এই যদি সেই বেড়াল, তবে মাংস কই? আর এই যদি সেই মাংস, তবে বেড়াল কই? তাহলে কি ঐ কনডরসে-র জুরি থিওরেম বাস্তব জগতে আর খাটে না?এবার তাহলে আরেকবার ঝালিয়ে নেওয়া যাক কনডরসে-র উপপাদ্যের অ্যাজাম্পশনগুলো। ভোটার-দের হতে হবে “স্বতন্ত্র”, “দক্ষ”, এবং “আন্তরিক”। এর সবকটিই বিভিন্ন গবেষকের, বিভিন্ন মহলের প্রশ্নের মুখে পড়েছে বারংবার, যাদের কেউ-কেউ সত্যিই মনে করেন, যে এগুলো একসাথে সত্যি হওয়া প্রায় সোনার পাথরবাটির মত ব্যাপার।এই যেমন ধরুন “দক্ষতা”! যদি সত্যিই এমন হয়, যে বেশির ভাগ লোকের-ই পছন্দ ভুল বিকল্পটিকে, অর্থাৎ অঙ্কের ফর্মুলায় ঐ pc < 1/2 হয়ে যায়? উপরের ছবিটির নিচের অর্ধেক দেখুন এইবার। হুহু করে কেমন গ্রাফ শূন্যের দিকে ছুটছে? অস্যার্থ, “ইনডিভিজুয়াল কম্পিটেন্স” অর্ধেকের কম হলে যত ভোটার বাড়বে তত বিপর্যয়, তত ভুল দিকে যাওয়ার রাস্তা মসৃণতর, সেইরকম কেসে শ্রেষ্ঠ জুরির সাইজ় মাত্র ১!আর, “স্বাতন্ত্র্য”? ঐটিকে পলিটিক্যাল সায়েন্টিস্ট ও অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানীরা আক্রমণ করেছেন মুহুর্মুহু। তাদের বক্তব্য, যদি সবার-ই এক-ই দিকে ‘সিস্টেম্যাটিক বায়াস’ থাকে, অথবা সবার কানে এক-ই প্রোপাগান্ডা পৌঁছয়? অথবা, সব ভোটারের খবরের সবটুকু অধিকার করে নেয় এক-ই উৎস থেকে আসা ফেক নিউজ বা মিসইনফর্মেশন? যদি সব্বার মধ্যেই এক-ই দিকে ধাবমান পক্ষপাত, একদেশদর্শিতা, এক-ই অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার? সংখ্যাগরিষ্ঠর মধ্যে বিষক্রিয়ার মতই যদি ছড়িয়ে পড়ে এক-ই বিদ্বেষ? তারা কি সকলে, প্রত্যেকে একা, না পুরোটাই কোনো একটা মতবাদের একটিই অঙ্গমাত্র? এ ভয় কনডরসে-রও ছিল, তিনি লিখেছিলেন গণতন্ত্রের রোগ এই, যে ‘masses suffer from great ignorance with many prejudices’! আজ থেকে আড়াইশো বছর পরেও সে কথা অশ্লীল রকমের সত্যি বলে মনে হয়। তবুও, সেই ‘শেষ সত্য’ নয়!আগেই লিখেছি, আবার-ও মনে করাই। কনডরসে-র জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ Esquisse যখন লিখছেন, তখন তিনি শাসকের চোখে দেশদ্রোহী। আত্মগোপন করে আছেন পরিবারের থেকে বহু দূরে কোথাও, মাথার উপর সাক্ষাৎ গিলোটিন। ভেবে আশ্চর্য লাগে, যে সেই অকল্পনীয় অবস্থায় নিশ্চিত মৃত্যুর অপেক্ষায় বসেও তিনি বলে যাচ্ছেন মানব সভ্যতার সামনে একটিই রাস্তা, সে রাস্তায় সাময়িক বাধাবিঘ্ন থাকলেও রাস্তাটার মুখ সোজা উপরের দিকে, যার শেষে আল্টিমেট পারফেকশন, অন্তিম পূর্ণতা, সে যেন এক ‘অন্তহীন নক্ষত্রের আলো’। এবং সেই শেষ সোপানে পৌঁছলে দেখা যাবে সেই বিশ্বে কোনো অসাম্য নেই, দেশে-দেশে, জাতিতে-জাতিতে মারামারি নেই, কারণ সেই সব-ই তো আসলে সভ্যতার প্রগতির পরিপন্থী! এই আকালেও তাই, আমার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়, ‘এই পথে আলো জ্বেলে—এ-পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে’।১৭৯৪ সালের ২৯শে মার্চ, ঠিক আজ থেকে ২৩০ বছর আগে, কনডরসের মৃত্যু হয় কারারুদ্ধ অবস্থায়, মৃত্যুর কারণ আজও অজানা, কেউ বলেন আত্মহত্যা, কেউ রাজনৈতিক খুন।এই লেখাটার আর কোথাও যাওয়ার নেই আপাতত, অতএব এখানেই ইতি টানছি। শেষ করবো কনডরসে-র একটি অসামান্য উক্তি দিয়ে, এই লেখকের ঘিঞ্জি আপিসের ঘিঞ্জি বোর্ডের এক কোণে যেটি জ্বলজ্বল করে অজস্র আঁকিবুকি আর ভুল থিওরেমের মাঝে। অন্ধকার ও ক্লান্ত রাত্রে নির্জন হাইওয়ে ধরে একলা বাড়ি ফেরার রাস্তায় বহুদূর দিগন্তের জনপদের টিমটিমে আলোর মত সে যেন আমাকে পথ দেখায়।“The truth belongs to those who seek it, not to those who claim to own it.”সূত্রঃDuncan Black et al. The theory of committees and elections. 1958.Marie Jean Antoine Nicolas De Marquis De Caritat Condorcet. Essai sur l’application de l’analyse `a la probabilit ́e des d ́ecisions rendues `a la pluralit ́e des voix. 1785.Francis Galton. Vox populi (1907) nature, n. 1949, vol. 75, pp. 450-451 (traduzione di romolo giovanni capuano©). Nature, 75:450–451, 1949.Robert E Goodin and Kai Spiekermann. An epistemic theory of democracy. Oxford University Press, 2018.Scott Hill and Renaud-Philippe Garner. Virtue signaling and the Condorcet jury theorem. Synthese, 199(5):14821–14841, 2021.Joan Landes. The history of feminism: Marie-jean-antoine-nicolas de caritat, marquis de condorcet. 2009.James Surowiecki. The wisdom of crowds. Anchor, 2005.Roman Vershynin. High-dimensional probability: An introduction with applications in data science, volume 47. Cambridge University Press, 2018.Kenneth F Wallis. Revisiting Francis Galton’s forecasting competition. Statistical Science, pages 420–424, 2014.ফেদেরিকো ফেলিনির চলচ্চিত্র – ধর্ম ও জীবন ভাবনা - শুভদীপ ঘোষ | ছবি: রমিত চট্টোপাধ্যায়স্টেট ও চার্চকে সম্পূর্ণ পৃথক করে দিতে হবে। রাজ্য পরিচালনার কাজে চার্চ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না এবং রাজ্যও চার্চের কাজে হস্তক্ষেপ করবে না। রাজ্য পরিচালনার কাজে রোমান ক্যাথলিক চার্চ সরাসরি হস্তক্ষেপ করত। নিয়ম-শৃঙ্খলা বলবৎ ছিল, যাকে বলা হত খৃষ্টীয় অনুশাসন। কিন্তু পরবর্তীতে স্টেট ও চার্চের এই বিযুক্তিকরণই ছিল সেকুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতার আদি সংজ্ঞা। নিয়ম-শৃঙ্খলা অর্থাৎ অনুশাসনের ভাবনা নিশ্চয়ই আদিম যুগে ছিল না, গুহামানবের যুগে ছিল না। জৈবিক বিবর্তনের পথ ধরে সমাজ তৈরি হয় এবং সেই পথেই কোনো একসময় নিশ্চয়ই নিয়ম- শৃঙ্খলা বা অনুশাসনের ভাবনা এসেছিল। ধর্মের উৎপত্তি ও সামাজিক অনুশাসন কি যমজ সন্তান! প্রাচ্যের প্রাচীন ধর্মগুলিই হোক বা আব্রাহামিক (সেমেটিক) ধর্মগুলিই হোক, পাপ-পুণ্যের ভয় দেখানো ব্যাপারটা ধর্মীয় অনুশাসন কায়েম রাখার পিছনে কাজ করত, তা হয়ত অস্বীকার করা যাবে না। ফলত সামাজিক অনুশাসন বা নিয়ম-শৃঙ্খলার প্রত্ন-রূপ হয়ত খুঁজে পাওয়া যাবে ধর্মীয় অনুশাসন গুলির মধ্যে! মনুসংহিতাতে আছে, ফ্রয়েড টোটেম এন্ড ট্যাবু-তেও উল্লেখ করেছেন এরকম বিধানের - মাতৃস্থানীয়া (মাসি পিসি কাকিমা জেঠিমা) কারো সাথে একই পথে যেতে যদি তোমার (মায়ের ছেলে) সাথে দেখা হয়ে যায় তাহলে তুমি তাঁর পায়ের পাতা ভিন্ন অন্য কোনো দিকে তাকাবে না, আর মাতৃস্থানীয়া ঢেকে নেবেন তাঁর মুখমণ্ডল! কিনসিপ বা আত্মীয়তা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনায় ক্লদ লেভিস্ত্রস সামাজিক বিভিন্ন বিধানের বিকাশের কেন্দ্রে রেখেছেন বিবাহ নামক অধুনা টলমলে ইন্সটিটিউশনটিকে। প্রমিসকিউটিকে আটকানোর প্রবল প্রচেষ্টা, অভিজ্ঞতা-নির্ভর বিধান বা অনুশাসনের সূচনা - এর মধ্যে মিশে আছে পাপ-পুণ্যের চেতনা। পাপ বা পুণ্য হবে, পাপ করলে শাস্তি পুণ্য করলে পুরস্কার, কিন্তু কে দেবে সেটা? এখানেই ঈশ্বরকে মাথায় নিয়ে ধর্মের অনুপ্রবেশ। আদিম মানুষের মাথায় ঈশ্বরের চিন্তা হয়ত আসেনি, তাদের ভয় ছিল পঞ্চভূতের প্রয়লঙ্কর রূপগুলি নিয়ে। যেহেতু তাতে মৃত্যু ছিল নিয়মিত ও অনিবার্য। কিন্তু ঐ অসহায়তাই একসময় তাদের ভাবতে বাধ্য করে অনন্ত ক্ষমতাশালী অতি-প্রাকৃতিক ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে। ব্যাপারটা এরকম দাঁড়ালো, ধর্মহীন সমাজ আসলে নিয়ম-শৃঙ্খলা-অনুশাসন-হীন ও ঈশ্বরহীন সমাজ। বলা-বাহুল্য সেকুলার (প্রবন্ধের প্রারম্ভে বলা অর্থে সেকুলার) সমাজ অনুশাসন-হীন, এটা আধুনিক রাষ্ট্র নিশ্চয়ই মনে করে না। অনুশাসন বলবৎ করার জন্য কোর্ট-পুলিশ আছে। কিন্তু এটাও নিশ্চয়ই বোঝা যাচ্ছে পুরো ব্যাপারটা বাইরে থেকে বলবৎ করা অনুশাসন নিয়ে নয়, ব্যক্তি ও সমাজ-মানসের স্বশাসিত নৈতিক অনুশাসনের এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। আব্রাহামিক ধর্মের সূচনা হয় ইহুদি ধর্ম বা জুডাইজমের দ্বারা। তৎপরবর্তী খৃস্টান ও সর্বশেষ ইসলাম। ক্রুশবিদ্ধ খৃষ্টের মিনিয়েচার ধর্মপ্রাণ খৃষ্টানদের গলায় গলায় আমরা ঝুলতে দেখি। ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরোর বিখ্যাত ক্রাইস্ট দা রিদিমার থেকে সর্বত্র আমরা দেখেছি স্থাপিত খৃষ্টকে। কিন্তু ফেলিনির La Dolce Vita (১৯৬০) শুরুর দৃশ্যটির কথা ভাবুন! রোম শহরের উপর দিয়ে হেলিকপ্টারে করে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ক্রাইস্ট দা রিদিমারের মত সর্বংসহায় ভঙ্গীর খৃষ্ট-মূর্তিকে। মার্শেলো ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের দেখতে পাওয়া যায় আরেকটা হেলিকপ্টারে। বিকিনি পরা অভিজাত রমণীদের প্রশ্নের উত্তরে তারা জানায় খৃষ্টকে পোপের কাছে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আসলে আমাদের মনে হয় পরিচালক যেন ইঙ্গিত করছেন, খৃষ্টের জন্য স্থাপন করার মত উপযুক্ত স্থান সারা শহরে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না! এই ছবির পরিচালক ফেদেরিকো ফেলিনি (১৯২০-১৯৯৩) তাহলে কোনদিকে ইঙ্গিত করছেন? ধর্মনিষ্ঠ অনুশাসন-যুক্ত সুশৃঙ্খল সমাজের দিকে নাকি ধর্মহীন অনুশাসন-হীন উৎশৃঙ্খল সমাজের দিকে? এটা বুঝতে গেলে জানতে হবে ধর্মের ব্যাপারে ফেলিনির মনোভাব কি ছিল? “It’s difficult biologically and geographically not to be a Catholic in Italy. It’s like a creature born beneath the sea – how can it not be a fish? For one born in Italy, it’s difficult not to breathe, from childhood onward, this catholic atmosphere. One who comes from Italian parents passes a childhood in Italy, enters the church as baby, makes his Communion, witnesses Catholic funerals – how can he not be a Catholic? Still, I have a great admiration for those who declare them selves a detached laity – but I don’t see how this can happen in Italy.” একে ধর্ম নিয়ে ফেলিনির সরাসরি মতামত বলা যাবে না। কিন্তু ফেলিনির এই উচ্চারণের মধ্যে নিহিত আছে আধুনিক মানুষের মধ্যে ধর্ম-বিশ্বাস কি ভাবে জন্মায় তার রহস্য। ধর্ম যেন, যাকে কার্ল ইয়ুং বলেছিলেন ‘সমষ্টিগত মগ্ন-চৈতন্য’ (collective unconscious), তার আওতাধীন! অর্থাৎ ধর্ম-বিশ্বাস আসলে আধুনিক মানুষ পায় ‘সমষ্টিগত মগ্ন-চৈতন্য’ থেকে। কেননা এটা দীর্ঘদিন ধরে লালিত হতে হতে ক্রমেই সমাজ-মানসের অংশ হয়ে গেছে। মানুষ যেন ধর্ম-বিশ্বাস নিয়েই জন্মায়। পরবর্তীকালে যুক্তি-বুদ্ধির চর্চার ফলে কারো কারো মনে ধর্ম নামক অপৌরুষেয় বিষয় নিয়ে প্রশ্ন ওঠে এবং তারা তখন নাস্তিকতার দিকে ঝোঁকে। নাস্তিকতা যেন স্বাভাবিকতার বিরুদ্ধে একটা লড়াই। ফেলিনির চলচ্চিত্রীয় শিকড় কিন্তু নিহিত ছিল বহুল প্রসিদ্ধ ইতালির নব্য-বাস্তববাদের অন্দরে। তাঁর শুরুর দিকের ছবিতে বিশেষত ১৯৫৭ সালের Night of Cabiria পর্যন্ত সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের চিত্রায়ন, স্বাভাবিক আলোয় শুটিং ও নন-অ্যাক্টরদের ব্যবহার করার যে ব্যাপারটা আমরা দেখতে পাই, বোঝা যায় সবটাই ইতালির নব্য-বাস্তববাদের প্রভাব। ইতালির নব্য-বাস্তববাদ সম্পূর্ণত মার্ক্সীয়-বীক্ষার ফসল এবং এর পুরোধা তাত্ত্বিক সিজার জাভাত্তিনি বলেছিলেন “there must be no gap between life and what is on the screen”। সত্যিকারের জীবন ও চলচ্চিত্রে-চিত্রিত জীবনের মধ্যে কোনো তফাৎ না থাকার ব্যাপারটা ফেলিনি নিয়েছিলেন বটে, কিন্তু এর সমান্তরালে তাঁর একটি নিজস্ব ধরনও গড়ে উঠছিল। তাঁর ছবিতে ক্রমেই ঢুকে পড়তে থাকে ‘সমষ্টিগত মগ্ন-চৈতন্য’র জায়গা থেকে রোমান ক্যাথলিসিজমের অনুকল্প, ধর্মীয় শুদ্ধির বিপরীতে যৌনতা নামক খ্রিষ্টীয় পাপের অনিবার্য হাতছানি এবং পঞ্চাশ-ষাটের দশকের অর্থ-প্রাচুর্যের ফলে ইতালির সমাজ-জীবনের হেডনিস্টিক প্রবণতা। এই সমস্ত বিষয়কে একসাথে ধরার জন্য ফেলিনি কার্নিভাল-সুলভ একধরনের নির্মাণ-শৈলী তৈরি করছিলেন। বিষয় ও নির্মাণ-শৈলীর এই যুগ্মই নব্য-বাস্তববাদকে অতিক্রম করে তাঁর স্বতন্ত্র একটি স্টাইলের জন্ম দিয়েছিল। ১৯২০ সালে ইতালির রোমানি শহরে রোমান ক্যাথলিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন ফেলিনি। তাঁর চিত্র-সমাহারে সরাসরি ভাবে বাইবেলের উল্লেখ যদিও দেখতে পাওয়া যায় না। কিন্তু ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয় ও মোটিফ ফিরে ফিরে আসে। তবে এসব কিছুই বলা-বাহুল্য রোমান ক্যাথলিক পরিবেশে বেড়ে ওঠা ফেলিনির নিজস্ব বিবলিক্যাল ব্যাখ্যা। যদিও তিনি লুই বুনুয়েলের মত খৃষ্টকে সরাসরি আক্রমণ করেন নি। খৃষ্ট সম্পর্কে তাঁর মত ছিল – “যীশুর প্রতি আমার বিশ্বাস আছে। মানবজাতির ইতিহাসে তিনি যে মহত্তম মানুষ তাই নয়, উপরন্তু প্রতিবেশীর জন্য যেই নিজেকে উৎসর্গ করে তাঁর মধ্যে তিনি বেঁচে থাকেন – এই বিশ্বাস।”। ব্যাবিলন থেকে প্যালেস্টাইন পর্যন্ত যে অঞ্চলের এককালে নাম ছিল ‘কানান’ সেখানে দীর্ঘদিন ধরে মানুষ এক মহাপুরুষের আবির্ভাবের জন্য অপেক্ষা করছিল। একে মেসিয়ানিজম বা মাহদীবাদ বলে। যীশু যখন নাজারেথে জন্ম গ্রহণ করেন তখন সেটা ছিল রোমক উপনিবেশ। এই রোমক উপনিবেশে ইহুদীরা দীর্ঘদিন একজন পরিত্রাতার কথা চিন্তা করতেন এবং তাঁর জন্য অপেক্ষা করতেন। অনেকে মনে করেন যীশু হচ্ছেন সেই পরিত্রাতা। অনেকে মনে করেন প্রাথমিক সময়ে যীশুর কাজের (ধর্মীয় নয়, রাজনৈতিক কাজের মধ্যে) মধ্যে একটা বৈপ্লবিক ব্যাপার ছিল কিন্তু পরের দিকে তিনি থিয়োক্রিটিক হায়্যারারকির সঙ্গে সমঝোতার পথে হাঁটেন। তাছাড়া স্ক্রিপচারে মাসিহার আগমনে সমাজে যে যে সুফল আসবে বলে লেখা ছিল, যীশুর আগমনের পর ইহুদীরা সেগুলি দেখতে পান নি। ফলে তাঁরা যীশুকে স্বীকার করে নিতে পারেন নি। বলা-বাহুল্য এই নিয়ে প্রভূত বিতর্ক আছে এবং সেটা আলাদা আলোচনার বিষয়। প্রসঙ্গে ফিরে বলা যায় বিবিধ ব্যাপারে স্বেচ্ছাচারিতা ও দ্বৈত-অবস্থানের জন্য রোমান ক্যাথলিক চার্চকে অনেক ক্ষেত্রেই ফেলিনি সমালোচনা করেছেন। ফলস্বরূপ চার্চের সেন্সর সরকারিভাবে তাঁর The Temptation of Dr. Antonio (Boccaccio 70 (১৯৬২) ছবির একটি গল্প) ও 8 & half (১৯৬৩)-কে ব্যান্ড করে। রক্ষণশীল গোষ্ঠীর সদস্যরা তাঁর অন্য ছবিগুলির ক্ষেত্রে অনেক সময়ই হলের বাইরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করত। ফেলিনির শুরুর সাদাকালো সাতটি ছবিতে খৃষ্টীয় নৈতিকতার দিক থেকে পীড়া, অপরাধ, ক্ষমা, অনুতাপ, এবং মুক্তির মত অনুষঙ্গ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এই ছবিগুলিতে রোমান ক্যাথলিক চার্চের কার্যকলাপকে প্রায়শই সন্দেহের চোখে দেখা হয়েছে। প্রথম ছবি The White Sheikh (১৯৫২)-এই ফেলিনির খৃষ্টীয় মনন-বিশ্বের জোরাল প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। The White Sheikh-এ দুটি গল্প সমান্তরালে এগোতে থাকে। প্রথম গল্পে সদ্য-বিবাহিত দম্পতি ওয়ান্ডা ও ইভানকে আমরা দেখতে পাই তারা প্রথম বারের জন্য রোমে এসেছে। ভ্যাটিকানের কর্মচারী ইভানের কাকাকে প্রভাবিত করার জন্য ইভান চায় তার স্ত্রী ওয়ান্ডার সঙ্গে পরিবারের সকলের আলাপ করিয়ে দিতে। কাকা ভ্যাটিকানের দর্শকবৃন্দের সম্মুখে পোপের সঙ্গে নব্য-দম্পতির আলাপের একটা সুযোগও করে দেন। দ্বিতীয় গল্পটি সোপ অপেরার হিরো White Sheikh-র সঙ্গে ওয়ান্ডার গোপন সাক্ষাৎ নিয়ে। White Sheikh-র সঙ্গে দেখা করার জন্য ওয়ান্ডা হোটেল থেকে পালিয়ে যায়। ইভান ওয়ান্ডাকে খুঁজতে শুরু করে এবং রোমের রাস্তায় তার সঙ্গে দুজন বেশ্যার দেখা হয়। এদের মধ্যে একজনের সঙ্গে ইভান রাত কাটায়। ইতিমধ্যে হাসপাতাল থেকে ইভানের কাছে খবর আসে যে ওয়ান্ডা আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে এবং এখন সে হাসপাতালে ভর্তি! ইভান হাসপাতালে যায় এবং তারা দুজনেই তাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ করতে থাকে। কিন্তু সত্যি তারা গোপনে কি করেছিল সেটা একে-অপরের কাছে প্রকাশ করে না। নবদম্পতি হাতে হাত ধরে বাকি দর্শকদের সঙ্গে যখন পোপের দিকে এগোতে থাকে তখন সেন্ট পিটার গির্জার ঘণ্টা বেজে ওঠে। তারা আসলে গোপনে কি করেছিল এটা না জেনেই একে-অপরকে ক্ষমা করে দেয় এবং ওয়ান্ডা তার স্বামী ইভানের দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে, “Ivan, mio sceicco bianco sei tu!” অর্থাৎ “তুমিই এখন আমার ওয়াইট সেইখ!”। প্রকৃতপ্রস্তাবে এই সুখী সমাপ্তি কিন্তু ঐ নবদম্পতির সরলতার পুনরর্পণ নয় বরং এ যেন চার্চ নামক প্রতিষ্ঠানের হাত ধরে তাদের গতানুগতিক বাস্তবতায় ফিরে আসার দ্যোতনা। দর্শক শুধুমাত্র জানে এরা আসলে গোপনে কি করেছিল। চার্চ সেই সবের গভীরে প্রবেশ না করেই উপর-উপর তাদের সরল বলে প্রতিপন্ন করে। ফেলিনি দেখাতে চান সাংগঠনিক ধর্ম কি ভাবে কাজ করে। চার্চ নৈতিকতার দিকে জোর দেয় কিন্তু তাদের উদ্বেগটা ভাসা-ভাসা। সত্যটাকে ধামাচাপা দেওয়া হয় শুধুমাত্র আদর্শ রোমান ক্যাথলিক দম্পতিকে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার জন্য। দুটি গল্প যেন ফেলিনি-কৃত দুটি বিশ্বের স্মারক। একদিকে ফেলিনির ছবির চরিত্রদের মনে হয়, নিজেদের মত ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। পরিচালক সেখানে একজন সাইলেন্ট অবজারভার, তাঁর চরিত্রগুলির উপর কোনোরকম নিয়ন্ত্রণ নেই। কিঞ্চিৎ খ্যাপাটে, অনেক সময় বহিরাগত এবং কখনো অতিরঞ্জিত এই সব চরিত্রদের প্রবৃত্তির তাড়নাকে ফেলিনি স্থাপন করেন কখনো সোপ অপেরার (The White Sheikh) প্রেক্ষাপটে, কখনো সার্কাসের (La Strada (১৯৫৪), I clown (১৯৭০)) প্রেক্ষাপটে, কখনো থিয়েটার বা ভ্যারাইটি সোয়ের (Variety Lights (১৯৫০)) প্রেক্ষাপটে, কখনো চলচ্চিত্রের/টেলিভিশনের (Intervista (১৯৮৭) , Ginger & Fred (১৯৮৬)) প্রেক্ষাপটে, কখনোবা অর্কেস্ট্রার (Orchestra Rehearsal (১৯৭৯)) প্রেক্ষাপটে। অন্যদিকে রয়েছে, ছবির চরিত্রগুলির জীবনযাত্রার বিপরীতে বহমান রোমান ক্যাথলিক চার্চের নিজস্ব নৈতিক অনুশাসনের ভাবনা। মুশকিল হল চার্চ চরিত্রগুলির কৃতকাজের মনস্তাত্ত্বিক জায়গাটি নিয়ে না ভেবেই নৈতিক অনুশাসন বলবৎ করার চেষ্টা করায়, সেটা চরিত্রগুলির অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপনের কোনো প্রকার সমাধান দিতে পারে না। সাদাকালো পর্বের প্রথম দিকের ছবিগুলিতে হ্যাপি এন্ডিংয়ের একটা ব্যাপার থাকলেও ঐ পর্বের শেষের দিকের ছবিগুলিতে প্রধান চরিত্রের নেতিবাচক পরিণতি প্রায়শই আমরা দেখতে পেয়েছি। অপরাধী ও নির্যাতিত – কারোর প্রতিই পরিচালক অতিরিক্ত আবেগ প্রদর্শন করেন নি। গরীব ও অসহায় চরিত্ররা খৃষ্টীয় অর্থে অশুভ শক্তির শিকার, কিন্তু তারা তখনো অলৌকিকের প্রতি আস্থাশীল। চরিত্রগুলির যন্ত্রণা ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট হিসেবে বিধৃত হওয়ায় ব্যাপারটা দর্শকের মনে গভীর সহানুভূতির সঞ্চার করেঅপরের প্রতি সহমর্মিতার যে ভাবনা খৃষ্টধর্মে আছে, নৈতিকভাবে ছবিগুলি সেই মূল্যবোধের দ্বারা চালিত। যন্ত্রণা, অনুতাপ ও মুক্তি – এই খৃষ্টীয় ভাবনা এখানে যুক্ত হয়ে আছে। La Starda ছবিটিতে যেরকম। তরুণী ভবঘুরে গেলসোমিনা (ফেলিনির স্ত্রী Giulietta Masina অভিনীত) সার্কাসের প্রধান জ্যাম্পানোর (Anthony Quinn অভিনীত) পাশবিক আচরণের শিকার হয়। এই জ্যাম্পানোকে ফেলিনি চিত্রিত করেছেন একেবারে আবেগ ও মনুষত্বহীন একজন পাশবিক প্রকৃতির মানুষ হিসেবে। একদা পরিত্যক্ত গেলসোমিনার মৃত্যুর খবর একদিন জ্যাম্পানোর কানে আসে। কি হয় এই মানুষটির? La Starda-র অসাধারণ অন্তিম দৃশ্যে মদ্যপ জ্যাম্পানোকে আমরা দেখতে পাই সমুদ্রের পাড়ে অন্ধকার রাত্রিতে কান্নায় ভেঙ্গে পড়তে। সমুদ্রের পাড়ে সুবিশাল আকাশের দিকে একবার তাকিয়ে জ্যাম্পানো ডুকরে কেঁদে ওঠে। কিন্তু ফেলিনি আমাদের আকাশটা দেখান না। সমুদ্রের পাড়ে শুধুমাত্র জ্যাম্পানোতে আবদ্ধ ফেলিনির ক্যামেরা অনুতাপকে এমন উচ্চতায় নিয়ে যায় যাকে শৈল্পিক সিদ্ধির চূড়ান্ত ছাড়া আর কিছু বলার থাকে না। অভিভূত আমরা শুধু বিস্ময়ে হতবাক হয়ে ভাবি কিভাবে এরকম পাশবিক একটি মানুষের মনের অন্দরে এরকম মানবিক একটা স্পন্দন জাগতে পারে? একার্থে গেলসোমিনা যেন খৃষ্ট নিজেই এবং গোটা ছবিটা যেন খৃষ্টীয় নীতিকথা। এই ছবিগুলি রোমান ক্যাথলিসিজমের প্রতীকে ঠাসা। La Starda-য় এক জায়গায় ক্রস ও খৃষ্টের স্ট্যাচু নিয়ে বিশাল একটি মিছিলের পাশে গেলসোমিনাকে দেখা যায় হাঁটু গেড়ে বসে আছে। পরে জ্যাম্পানোর সঙ্গে যাত্রার সময় একটি মঠে একজন সহৃদয় নানের সঙ্গে গেলসোমিনার পরিচয় হয়। এই মঠে যাত্রীরা রাত্রি যাপন করে। গেলসোমিনা ভীষণ শান্তি বোধ করে ঐ মঠে রাতযাপনের সময় এবং পরের দিন মঠ ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় সে কেঁদে ফেলে। The Swindle (১৯৫৫) ছবিতে পিকাসো নামক একটি চরিত্র ভার্জিন মেরীর একটি স্ট্যাচু দেখতে পায়। স্ত্রীকে মিথ্যে কথা বলার জন্য পিকাসো ঐ স্ট্যাচুর সামনে অনুশোচনা করতে থাকে। একটু পরে চার্চের ঘণ্টা বেজে উঠলে সে বাড়ি চলে যায়। The night of Cabiria (১৯৫৭) ছবিতে ভার্জিন মেরীর একটি প্রার্থনাস্থলের অভিমুখে আগত তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে বেশ্যা ক্যাবিরিয়া (ফেলিনির স্ত্রী Giulietta Masina অভিনীত) যোগ দেয়। তীর্থযাত্রীরা নতুন জীবনের অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে মোমবাতি জ্বালিয়ে মেরীর চার্চের দিকে এগোতে থাকে। ক্যাবিরিয়া মেরীর ছবির সামনে প্রার্থনা করতে থাকে যাতে তার জীবনেও পরিবর্তন আসে। কিন্তু আচারানুষ্ঠানটির পরে সে অনুভব করে কোনো মিরাকল ঘটে নি তাই তার জীবনের পরিবর্তনের কোনো সম্ভাবনাই নেই। মধ্য-পঞ্চাশের দশক থেকে ইতালির অর্থনীতিতে জোয়ার আসে। নব্য-বাস্তববাদকে আত্মস্থ করে ফেলিনির স্বতন্ত্র স্টাইল আরো ঘনীভূত হতে থাকে। তথাপি, ১৯৬০-র La Dolce Vita-তে বা ১৯৬২-র The Temptation of Dr. Antonio-তে বা ১৯৬৩-র 8 & half-এ রোমান ক্যাথলিসিজমের চিহ্ন বিদ্যমান এবং সমালোচনা এখানে আরো বেশি স্পষ্ট। এই আলোচনার শুরুর La Dolce Vita-র সেই যীশুকে হেলিকপ্টারে করে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার দৃশ্যে ফিরে আসা যাক। ১৯৫৭ সালের পয়লা মে, যীশুর একটি বিশাল স্ট্যাচুকে সত্যিই হেলিকপ্টারে করে সেন্ট পিটার স্কোয়ারে নিয়ে আসা হয়েছিল। চলচ্চিত্রে প্রদর্শিত এই দৃশ্যটির দিকে ভালো করে তাকালে আমরা দেখতে পাবো ফেলিনির স্বতন্ত্র স্টাইল এখানে রোমের আইডেন্টিটির তিনটি দিককে একসঙ্গে ধরেছে। পিছনে কলসিয়ামের মত ধ্বংসাবশেষ রোমের পরম্পরাগত অতীতের প্রতীক, হেলিকপ্টারটি হল অর্থনৈতিক ভাবে সমৃদ্ধ হেডনিস্টিক বর্তমানের প্রতীক এবং রোমান ক্যাথলিক আইডেন্টিটির প্রতীক হলেন ঝুলন্ত খৃষ্ট। এই তিনটি বিষয়ের ঘাত-প্রতিঘাত ধরেই যে ছবিটি পরবর্তীতে অগ্রসর হবে ফেলিনি শুরুতেই তার ইঙ্গিত দিয়ে দেন! নব্য-বাস্তববাদী চলচ্চিত্রগুলিতে মূলত চিত্রিত হয়েছে - অর্থনৈতিক দুর্দশা জনিত সামাজিক বিশৃঙ্খলা এবং সেখানে চার্চ অনেকাংশেই উপশম ও আশার প্রতীক। ফিয়েট অটোমোবাইল, ভেস্পা স্কুটার ও অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী রপ্তানি করে মধ্য-পঞ্চাশ থেকে ইতালির অর্থনীতি সমৃদ্ধ হতে থাকে। একই সঙ্গে কমতে থাকে চার্চে যাওয়া মানুষের সংখ্যা এবং বাড়তে থাকে হেডনিস্টিক জীবনযাপনের প্রতি উদগ্র টান। ১৯৫৬ থেকে ১৯৬২ সাল, চার্চে যাওয়া মানুষের সংখ্যা ৬৯% থেকে কমে দাড়ায় ৫৩%-এ। চার্চ ছেড়ে বিনোদনের দিকে ঝোঁকার এই প্রবণতাকে ফেলিনি যতটা ক্যাথলিক চার্চের অধঃপতন হিসেবে দেখেছেন তার চেয়ে অবশ্য অনেক বেশি দেখেছেন চার্চের প্রতি আনুগত্য-হীনতা ও ধার্মিকতার প্রতি বীতরাগ হিসেবে। ফেলিনির দৃষ্টিতে ধর্মের চিহ্ন হিসেবে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি তখনো সমাজের আগ্রহ ছিল বটে, কিন্তু সেই চিহ্নগুলির অন্তর্নিহিত অর্থের প্রতি কোনো আগ্রহই তখন আর অবশিষ্ট নেই। আধুনিক সমাজের কাছে ধর্ম একটা স্পেক্টাক্যালের বেশি কিছু নয়, বিনোদন মাত্র! La Dolce Vita-র শুরুতে হেলিকপ্টার সমেত ঝুলন্ত যীশুর ছায়া দেখতে পাওয়া যায় নতুন বহুতল বিল্ডিংয়ের গায়ে। বাচ্চা ছেলেরা (আগামী প্রজন্মের প্রতীক) সেটা দেখার জন্য দলে দলে দৌড়তে থাকে। এই দৃশ্যটি একই সঙ্গে দুটি জিনিসকে প্রতিকায়িত করে। এক, ধর্ম এখন স্পেক্টাক্যাল হিসেবে কাজ করছে, বিনোদন হিসেবে বাচ্চারা সেদিকে দৌড়চ্ছে। দুই, ক্যাথলিসিজমের মধ্যে সত্যি একটা স্পেক্টাক্যালের ব্যাপার আছে - গির্জাগুলির সুবিশাল উপস্থিতি, যীশুর প্যাশন, এগুলিকে ঘিরে পবিত্র দিনের উৎসব। আগামী প্রজন্ম বিশ্বাসের ছায়ায় বড় হয়েছে, স্পেক্টাক্যাল রয়ে গেছে, কিন্তু অবয়বটা আর নেই। আজকের দিনে যাকে ড্রোন শট বলে অনেকটা সেই ভঙ্গিতে ঝুলন্ত যীশুর হেলিকপ্টারটিকে রোম শহরের উপর দিয়ে উড়ে যেতে দেখা যায়। নীচে ঝাঁ চকচকে আধুনিক ঘরবাড়ি কলকারখানা পরিলক্ষিত হয়। দুজন গৃহ-নির্মাণকর্মীকে দেখা যায় উড়ন্ত হেলিকপ্টারের দিকে হাত নেড়ে টাটা করতে। খৃষ্টধর্মের প্রভাবের ক্রমক্ষয়িষ্ণুতা এবং কন্সিউমার-সংস্কৃতির ক্রমবর্ধমান প্রভাবের সূচক এই দৃশ্যগুলি। দুই গৃহ-নির্মাণকর্মী আক্ষরিক অর্থেই যেন হাত নেড়ে ক্যাথলিসিজমকে বিদায় জানায়। অতঃপর মার্সেলো রুবিনি (Marcello Mastroianni অভিনীত) ও পাপারাজ্জিদের হেলিকপ্টারটিকে প্রথমবারের জন্য দেখা যায়। যীশুকে ছেড়ে সিউমিংপুলের ধারে শুয়ে থাকা মেয়েদের দিকে তারা এগিয়ে যায়। খৃষ্টধর্ম থেকে বিযুক্তি এবং শারীরিক সুখের দিকে ধাবমান আধুনিক মানুষের প্রতীক-হিসেবে রুবিনি ও পাপারাজ্জিরা প্রথমেই চিহ্নিত হয়। কিন্তু মেয়েগুলি রুবিনিকে তাদের ফোন-নম্বর দিতে অস্বীকার করে। এই প্রত্যাখ্যানই আসলে রুবিনির ভবিতব্য, সারা ছবিজুড়ে আমরা সেটাই দেখবো। শারীরিক সুখ বা হেডনিস্টিক প্রবণতা যে খৃষ্টীয় আদর্শের বিপরীত এই ব্যাপারটাও এই ছবির প্রধানতম বক্তব্যগুলির একটি। বিত্ত-বৈভব যখনই সমাজে বেড়েছে হেডনিজম মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, এটা ইতালির সমাজে বহুকাল ধরেই পরিলক্ষিত। Gaius Petronius-র রচনা Satyricon থেকে ফেলিনি ১৯৭০ সালে Fellini Satyricon নামে একটি ছবি করেন। ছবিটি সম্রাট নিরোর সময়কালকে এই হেডনিজামের প্রেক্ষাপটে ধরে। রুবিনির সঙ্গে তার প্রেমিকা এম্মার সম্পর্ক মনস্তাত্ত্বিক-সমস্যার ঘেরাটোপে বন্দি। এম্মা অন্য-নারীদের সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারে রুবিনিকে ক্রমাগত সন্দেহ করে যায় । ব্যাপারটা অমূলকও নয়। আমরা রুবিনিকে দেখেছি ধনী ম্যাদালেনার (Anouk Aimée অভিনীত) সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কে জড়াতে। সুইডিশ-আমেরিকান চিত্রতারকা সিল্ভিয়ার (Anita Ekberg অভিনীত) প্রতি রুবিনির লালসা বিখ্যাত নৈশ-অভিযানের দৃশ্যে পরিলক্ষিত। কিন্তু রুবিনির সেই লালসা চরিতার্থ হয় না। শারীরিক সুখের সন্ধানে রুবিনির এই একের পর এক প্রচেষ্টা আসলে শরীর-সর্বস্ব আধুনিক সভ্যতার ব্যর্থ সুখানুসন্ধান। ট্রেভি ফাউন্টেইনের জলধারা বন্ধ হয়ে যায়। কিংকর্তব্যবিমুঢ় ও দিকভ্রান্ত আধুনিক সমাজের প্রতীক রুবিনি ও সিল্ভিয়ার দিকে সাইকেল আরোহীসহ ছবির সমস্ত দর্শককুল যেন অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। এদিকে রোমান ক্যাথলিসিজমের অবস্থানটা কি? দুটি বাচ্চার কাছে ভার্জিন মেরীর অলৌকিক চেহারা প্রকাশিত হয়েছে - এম্মার পীড়াপীড়িতে রুবিনি ও এম্মা সেটা দেখতে শহরতলীতে যায়। এম্মার আশা এই উপলক্ষে যদি তাদের সমস্যাসঙ্কুল সম্পর্কেরও একটা মির্যাক্যাউলাস সমাধান ঘটে। কিন্তু এই গোটা ব্যাপারটাই সিরিয়াসনেস হারিয়ে দেখা যায় আদতে একটি টেলিভিশন ইভেন্টে রূপান্তরিত হয়েছে! পাপারাজ্জিরা চারিদিকে থিকথিক করছে। এদিকে একটি অসুস্থ মেয়েকে তার মা বাঁচার আশায় নিয়ে আসে। কিন্তু মেয়েটি মারা যায়। ভার্জিন মেরী কেন, কোন মিরাকলই ঘটে না। উপরন্তু অসুস্থ মেয়েটির মৃত্যুতে শোকাহত সকলে পরের দিন ভোর বেলা দেখতে পায় একজন পাদ্রি মেয়েটির মৃতদেহের পাশে বসে শোকগাথা পাঠ করছে! ফেলিনি যেন দেখাতে চান মৃত মানুষের প্রতি সন্মান-সহমর্মিতায় সাঙ্ঘঠনিক ধর্মের দিক থেকে কোনো অভাব নেই বটে, কিন্তু মিরাকল হল অসহায় মানুষের সর্বশেষ আশা যা ব্যর্থ হবে জেনেও সাঙ্ঘঠনিক ধর্ম তা প্রচার করে থাকে। মার্সেলো রুবিনি বস্তুত ফেদেরিকো ফেলিনিরই অল্টার-ইগো। গসিপ সাংবাদিকতার বাইরেও রুবিনির একটা সাংস্কৃতিক সত্তা আছে। সে একজন বড় উপন্যাসিক হতে চায়। সাংস্কৃতিক-অভিজাতদের সংস্পর্শে থাকার তার একটা বাসনা আছে। রুবিনি তার বন্ধু স্টেইনারকে খুবই সম্মান করে। রুবিনির চোখে স্টেইনার ‘আদর্শ মানুষ’। শৈল্পিক উপাদানে সুসজ্জিত স্টেইনারের প্রসাদপম বাড়ি, বুদ্ধিজীবী বন্ধুদের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকা, তদুপরি তার অপূর্ব স্ত্রী ও দুই সন্তান – রুবিনির কাছে প্রকৃত অর্থে ‘La dolce vita’ বা ‘মিষ্টি জীবন’। রুবিনি ও এম্মা যেদিন স্টেইনারের বাড়িতে যায় সেদিন রুবিনি স্টেইনারকে বলে, “Your home is a refuge. Your children, your wife, your books, your extraordinary friends. I am wasting my life. I am not going anywhere. I had ambitions once…”। রুবিনি আসলে তার জীবনযাত্রার অন্তঃসারশূন্যতা অনুভব করে । কিন্তু চার্চে যাওয়া স্টেইনার প্রত্যুত্তরে অপ্রত্যাশিত ভাবে বলে, “Don’t do what I have done … I fear peace more than anything else. It seems to me like it’s a façade with hell hiding behind it.”। স্টেইনারের প্রতিক্রিয়ার মধ্যে কিরকম একটা অস্বস্তি রয়েছে। স্টেইনারের জীবন আপাতদৃষ্টিতে সুখী ও আকর্ষণীয় লাগলেও, বোঝা যায় অন্তরালে কোথাও একটা গভীর দুঃখ-কষ্ট আছে। স্টেইনার যেন রোমের চাকচিক্যময় সমাজের পিছনের নৈতিক ভঙ্গুরতার প্রতীক। স্টেইনার তার দুই সন্তানকে মেরে নিজে আত্মহত্যা করে! ধর্মনিষ্ঠ অনুশাসন-যুক্ত সমাজ নাকি ধর্মহীন অনুশাসন-হীন উৎশৃঙ্খল সমাজ – এরকম কোনো বাইনারিতে কি আদৌ পৌঁছান সম্ভব? স্টেইনারের পরিণতি রুবিনির শেষ আশা ও বিশ্বাসের জায়গাটাকেও ধস্ত করে দেয়। উদ্দাম রাত্রি-শেষে ভোরবেলা রুবিনি যখন সমুদ্রের পাড়ে এসে দাঁড়ায়, মাঝিরা তখন একচোখ খোলা একটা বড় জেলি-মাছকে পাড়ে এনে তুলেছে। ফেলিনি এরপর রচনা করেন পৃথিবীর চলচ্চিত্রের ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ক্লাইম্যাক্সটি। ঋত্বিক ঘটক যাকে মাইলেকেঞ্জেলোর ভাস্কর্যের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন, La dolce vita-র সেই একমাত্র সরল-নিষ্পাপ মেয়েটি অন্তিম দৃশ্যে রুবিনিকে হাত নেড়ে ডাকে। ধর্ম-অধর্মের সীমানা ছাড়িয়ে যাবতীয় নৈরাশ্যকে অতিক্রম করে শাশ্বত মানবতার কাছে পৌঁছান ছাড়া আমাদের যে আর কোনো গত্যন্তর নেই।
হরিদাস পালেরা...
মহাবিশ্বের রহস্য - অনির্বাণ কুণ্ডু | রাতের তারা ঝলমলে আকাশ তো সবাই দেখেছো। অতি প্রাচীনকালেও মানুষ দেখতো, দেখে মুগ্ধ হতো, আর এই জ্যোতিষ্কদের রহস্য ভেদ করার চেষ্টা করতো। জ্যোতির্বিদ্যা মানুষের প্রথম বিজ্ঞান। আমাদের সেই গুহাবাসী কিংবা সদ্য কৃষিকাজ শেখা পূর্বপুরুষদের খালি চোখে আকাশ দেখার দিন থেকে আমরা অনেক এগিয়ে এসেছি। বিজ্ঞানের উন্নতি হয়েছে, যন্ত্রের উন্নতি হয়েছে, আমাদের দেখার এবং বোঝার ক্ষমতা অকল্পনীয়ভাবে বেড়েছে। তার সঙ্গে বেড়েছে নতুন নতুন উত্তর-না-জানা প্রশ্নের দল। ভাগ্যিস বেড়েছে, কারণ প্রশ্ন না থাকলে—সবই জানা হয়ে গেলে—বিজ্ঞানের তো আর কোনো আকর্ষণই থাকত না! আজ তোমাদের অল্প করে এরকম কয়েকটা উত্তর-না-জানা প্রশ্নের কথাই বলব। পৃথিবীর বহু বিজ্ঞানী এসব প্রশ্নের উত্তর জানার চেষ্টা করে চলেছেন, মানুষের সভ্যতার এ এক অনন্য অ্যাডভেঞ্চার। আশা করব, একদিন তোমরাও এই অ্যাডভেঞ্চারে যোগ দেবে।তোমরা জানো, আমরা খালি চোখে যে সব তারা দেখতে পাই, সবাই একটি তারকাপুঞ্জ বা নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে আছে। এই তারকাপুঞ্জ বা গ্যালাক্সির নাম মিল্কি ওয়ে, বাংলায় ছায়াপথ। আমাদের সূর্য ছায়াপথের এক ধারে পড়ে থাকা একেবারেই সাধারণ একটি তারা। সূর্যের চেয়ে বহুগুণ উজ্জ্বল, বহুগুণ বড়, আর বহুগুণ গরম তারা যেমন আছে, তেমনি সূর্যের চেয়ে ছোট এবং নিষ্প্রভ তারাও নেহাৎ কম নেই। ছায়াপথে যে কত তারা আছে, তা আমরা আজও ঠিকভাবে গুনে উঠতে পারিনি, তবে সংখ্যাটা বিশাল, দশ হাজার কোটি (অর্থাৎ একের পিঠে এগারোটা শূন্য, ১০১১) থেকে চল্লিশ হাজার কোটির মধ্যে কিছু একটা। বুঝতেই পারছ, এর অতি সামান্য সংখ্যক তারাই আমাদের খালি চোখে ধরা পড়ে।এইমাত্র একটা বিরাট বড় সংখ্যা পেলাম, কিন্তু ঘাবড়ে গেলে চলবে না—আকাশ এবং মহাবিশ্ব নিয়ে কথা বলতে গেলে এরকম বিরাট বিরাট সংখ্যারা মাঝেমধ্যেই উঁকি দেবে। দূরত্ব মাপার একক দিয়েই শুরু করি। আলো মহাশূন্যে এক সেকেন্ডে তিন লক্ষ কিলোমিটার যায়, সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে প্রায় আট মিনিট লাগে। এক বছরে আলো যতটা পথ পাড়ি দেয়, তাকে বলে এক আলোকবর্ষ। মহাবিশ্বের হিসেবে এটা নিতান্তই চুনোপুঁটি দূরত্ব, আমাদের সবচেয়ে কাছের তারাও চার আলোকবর্ষের বেশি দূরে। বিজ্ঞানীরা আর একটা একক ব্যবহার করেন, পার্সেক—এক পার্সেক প্রায় সোয়া তিন আলোকবর্ষের সমান। ১০০০ পার্সেকে এক কিলোপার্সেক, আর দশ লক্ষ পার্সেকে এক মেগাপার্সেক। মেগাপার্সেক দূরত্বের বৃহত্তম একক, এক মেগাপার্সেক যেতে আলোরও প্রায় সাড়ে বত্রিশ লক্ষ বছর লাগে।ছায়াপথ কিছু একমাত্র গ্যালাক্সি নয়। এর ধারেকাছে আরো অনেকগুলো গ্যালাক্সি আছে, যেমন বড় ও ছোট ম্যাগেলানিক মেঘ, বা অ্যান্ড্রোমিডা। এরকম মোট কত গ্যালাক্সি আছে? বিজ্ঞানীদের অনুমান, প্রায় দশ হাজার কোটি। এটা হল যতটুকু মহাবিশ্ব আমরা দেখতে পাই, তার হিসেব, এর বাইরে মহাবিশ্বের আরো বিরাট অংশ হয়তো পড়ে আছে যা আমরা দেখতেই পাই না। কেন পাই না? কারণ সেখান থেকে আলো এখনো আমাদের কাছে এসে পৌঁছতেই পারেনি। মহাবিশ্বের বয়েস প্রায় চোদ্দশো কোটি বছর (এই হিসেবটাও বিজ্ঞানীরা খুব নিখুঁতভাবে বের করেছেন), সুতরাং দু হাজার কোটি আলোকবর্ষ দূরের গ্যালাক্সি থেকে তো আলো এখনো আমাদের কাছে এসে পৌঁছবে না। ছবি – ১: আমাদের প্রতিবেশী গ্যালাক্সি অ্যান্ড্রোমিডা। ছায়াপথের মত এটিও একটি প্যাঁচ খাওয়া বা স্পাইরাল গ্যালাক্সি। মাঝে একটা ভারি অংশ, যার চারদিকে আছে কয়েকটি স্পাইরাল বাহু। ছায়াপথের এরকম একটি স্পাইরাল বাহুর মধ্যে আছে আমাদের সূর্য এবং সৌরজগৎ, ধীরে ধীরে কেন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে। (সূত্র: David Dayag)আলোর কথা বললামই যখন, একটু মনে করিয়ে দিই – আলো হল তড়িৎচৌম্বকীয় তরঙ্গ, আর দৃশ্যমান আলোর বাইরেও এক বিরাট বর্ণালী পড়ে আছে। তরঙ্গদৈর্ঘ্য বাড়ালে পাব অবলোহিত (যাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন লাল-উজানি আলো), তারপর মাইক্রোওয়েভ, রেডিওতরঙ্গ। কমের দিকে অতিবেগুনি, এক্সরশ্মি, গামারশ্মি। এদের সবাইকেই আমরা আলো বলব। মহাকাশ থেকে সব রকম আলোই আসে, কম তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে শোষিত হয়ে যায় (না হলে প্রাণের সৃষ্টিই হত না), কাজেই সেই সব আলো ধরতে গেলে পৃথিবীর কক্ষপথে, বায়ুমণ্ডলের বাইরে, দূরবীন বসাতে হয়। হাবল্ স্পেস টেলিস্কোপ হল কক্ষপথে বসানো প্রথম দূরবীন, মহাবিশ্বের কত খবর যে আমরা হাবল্ টেলিস্কোপের থেকে পেয়েছি তার ইয়ত্তা নেই। জ্যোতির্বিজ্ঞানী এডউইন হাবলের নামে এই টেলিস্কোপ, তাঁর কথায় একটু পরেই আমরা আসব। ছবি – ২: হাবল স্পেস টেলিস্কোপ। ১৯৯০ সালে একে পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপন করা হয়, তিরিশ বছর ধরে মহাবিশ্বের পুঙ্খানুপুঙ্খ ছবি পাঠিয়ে চলেছে। (সূত্র: Ruffnax (Crew of STS-125))তোমরা সবাই জানো, মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম একক হল পরমাণু। এক সময় বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করতেন, পরমাণু অবিভাজ্য, তাকে আর ভাঙা যায় না, কিন্তু পরে টমসন, এবং রাদারফোর্ড ও তাঁর সহযোগীরা দেখালেন যে পরমাণুকে ভাঙা যায়। পরমাণুর মূল উপাদান তিনটে – কেন্দ্রে ধনাত্মক তড়িৎবাহী প্রোটন এবং তড়িৎনিরপেক্ষ নিউট্রন, আর বাইরে ঋণাত্মক তড়িৎবাহী ইলেকট্রন। সবচেয়ে সহজ পরমাণু হল হাইড্রোজেন গ্যাসের, এর কেন্দ্রে থাকে শুধু একটা প্রোটন, আর বাইরে একটা ইলেকট্রন। হিলিয়ামের কেন্দ্রে আছে দুটো করে প্রোটন আর নিউট্রন। যে কোন মৌলের পরিচয় তার কেন্দ্রে প্রোটনের সংখ্যা দিয়ে ঠিক হয়, নিউট্রনের সংখ্যার একটু এদিক ওদিক হতে পারে, হলে একই মৌলের বিভিন্ন আইসোটোপ পাওয়া যায়।বিজ্ঞানীরা বলেন, এক প্রচণ্ড শক্তিশালী বিস্ফোরণে মহাবিশ্বের সৃষ্টি। এই মহাবিস্ফোরণের চলতি নাম হল বিগ ব্যাং। আমরা যে সমস্ত পদার্থ চারপাশে দেখতে পাই, মহাবিশ্ব সৃষ্টির মুহূর্তেই তারা মোটেই তৈরি হয়নি। প্রথম হাইড্রোজেন পরমাণু পেতে আমাদের প্রায় চার লক্ষ বছর অপেক্ষা করতে হবে। নক্ষত্র সৃষ্টি হতে তখনো ঢের দেরি। মহাবিশ্বে আমরা যত পরমাণু দেখতে পাই (বা আছে বলে অনুমান করতে পারি), তার মোট ভরের চুয়াত্তর শতাংশই হাইড্রোজেন। আর চব্বিশ শতাংশ হিলিয়াম। তিন নম্বরে অক্সিজেন, এক শতাংশের সামান্য বেশি। বাকিরা নেহাৎই নগণ্য। এর পরের সাতটা স্থানে আছে কার্বন, নিয়ন, লোহা, নাইট্রোজেন, সিলিকন, ম্যাগনেসিয়াম, আর সালফার, তাদের মোট অবদান আধ শতাংশও হয় কিনা সন্দেহ। এখানে বলে রাখা ভালো, হাইড্রোজেন আর হিলিয়াম ছাড়া বাকি যে সব মৌলের নাম করলাম, সবাই তৈরি হয়েছে কোনো না কোনো নক্ষত্রের ভেতরে। অর্থাৎ, আমরা সবাই বহুকাল আগে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া কোনো তারার ধ্বংসাবশেষ।দুইয়ের পিঠে তিরিশটা শূন্য বসালে যা হয় (২ X ১০৩০), সূর্যের ভর প্রায় অত কিলোগ্রাম। আগেই বলেছি, মহাবিশ্বে সুর্য নিতান্তই গড় মাপের একটি তারা, আর মোট তারা আছে প্রায় একের পিঠে বাইশটা শূন্য। তাহলে যা পাওয়া গেল, সেটাই কি মহাবিশ্বের মোট ভর? উত্তর, একেবারেই না। সব পরমাণুর অতি সামান্য একটা অংশই তারাদের মধ্যে থাকে, বাকিটা ছড়িয়ে থাকে বিভিন্ন গ্যালাক্সির মধ্যে, মহাজাগতিক ধূলিকণা বা মেঘ হিসেবে। এই মেঘের ঘনত্ব হিসেব করে মহাবিশ্বের সমস্ত পরমাণুর মোট ভর বিজ্ঞানীরা বের করেছেন --- একের পিঠে তিপ্পান্নটা শূন্য বসালে যত হয় (১০৫৩), প্রায় তত কিলোগ্রাম। বললাম না, আমাদের অনেক বড় বড় সংখ্যা নিয়ে কাজ করতে হবে? সে যাই হোক, এই সংখ্যাটাকে আমরা বলব দৃশ্যমান ভর। অদৃশ্য ভরও আছে। এই অদৃশ্য ভর থেকেই আমাদের গল্পটা শুরু হল। আমাদের পিছিয়ে যেতে হবে একশো বছরেরও বেশি আগে, ১৯১৪ সালে, যখন অ্যালবার্ট আইনস্টাইন মহাকর্ষ সম্বন্ধে তাঁর তত্ত্ব উপস্থাপিত করেন। এই তত্ত্বের নাম সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ, ইংরেজিতে জেনারেল রিলেটিভিটি। এর জটিল অঙ্ক আলোচনার কোন জায়গাই এখানে নেই, সে সব তোমরা বড় হয়ে পড়বে। কিন্তু মূল কথাটা একটু বুঝে নেওয়া যাক।এর আগে ১৯০৫ সালে আইনস্টাইন তাঁর বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ বা স্পেশাল রিলেটিভিটি প্রকাশ করেন। এই তত্ত্বের একটা অনুসিদ্ধান্ত হল, মহাশূন্যে আলোর চেয়ে বেশি বেগে কেউ যেতে পারে না (মহাশূন্যে কথাটা গুরুত্বপূর্ণ; জলের মধ্যে আলোর যা বেগ, তাকে দ্রুতগামী ইলেকট্রন হার মানাতে পারে), অর্থাৎ বহুদূরের খবর আনার জন্যে আলোর চেয়ে উপযুক্ত মাধ্যম আর কেউ নেই। আরেকটা বড় অনুসিদ্ধান্ত তোমরা সবাই জানো, যাকে গাণিতিকভাবে প্রকাশ করে যায়: E = mc2. এর মানে হল, ভরকে শক্তিতে বা শক্তিকে ভরে রূপান্তরিত করা যায়। পরমাণু বোমা বা পরমাণু চুল্লি যে শক্তি উৎপাদন করে, তা ইউরেনিয়াম বা প্লুটোনিয়াম জাতীয় তেজস্ক্রিয় পদার্থের খুব সামান্য কিছু ভরের শক্তিতে রূপান্তরের ফল। সূর্যের আলো ও তাপের পেছনেও এই সমীকরণ। নক্ষত্রের মধ্যে চারটে হাইড্রোজেনের নিউক্লিয়াস (অর্থাৎ প্রোটন) জুড়ে হিলিয়ামের নিউক্লিয়াস বা আলফা কণা তৈরি হয়। এতে সামান্য যে ভরের ঘাটতি পড়ে, সেটাই শক্তি হয়ে বেরিয়ে আসে। অত সামান্য ভর থেকে অত বিপুল শক্তি কোত্থেকে আসে? ওই যে আলোর বেগের বর্গ বা c2 দিয়ে গুণ করা আছে।কিন্তু বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের আসল জিনিসটাই তো বলা হয়নি। আমরা ছোট থেকে শিখে আসি – দেশ বা স্থানের তিনটে মাত্রা, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, আর উচ্চতা; আর কাল বা সময়ের একটাই মাত্রা, যাকে ঘড়ি দিয়ে মাপি। আইনস্টাইন দেখালেন, যে, দেশ আর কালকে এভাবে আলাদা করা যায় না, আমাদের মোট চার মাত্রার দেশকালের কথা বলা উচিত। এই যে দেশ আর কালের মাত্রা মিলেমিশে গেল – এটা ধরা পড়বে, যদি কোনো বস্তুর বেগ আলোর বেগের কাছাকাছি হয়, তবেই। দৈনন্দিন জীবনে দেশ আর কাল সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস।পৃথিবীর চারদিকে চাঁদের ঘোরাই বলি, বা সৌরজগৎ, বা গ্যালাক্সিদের মহাশূন্যে ঘুরে বেড়ানো, মহাবিশ্বের আসল চালিকাশক্তি হল মহাকর্ষ বল। এই বল কীভাবে কাজ করে, বহুদিন আগেই আইজাক নিউটন তা বলে গেছেন --- দুটি বস্তুর ভরের গুণফলের সমানুপাতিক, আর তাদের দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক। বিভিন্ন পর্যবেক্ষণে এই সূত্রের সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে, যেমন একেবারে নির্ভুলভাবে গ্রহণের সময় বা গ্রহদের কক্ষপথের গণনা।আইনস্টাইন তাঁর সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদে বললেন, মহাকর্ষ আসলে কোনো বলই নয়। তাহলে কী? আইনস্টাইন বললেন, মহাকর্ষ আসলে চার মাত্রার এই দেশকালের জ্যামিতির খেলা। কাগজের ওপর দু-মাত্রার ইউক্লিডিয়ান জ্যামিতি আমরা সবাই স্কুলে করেছি, তোমরা কেউ কেউ হয়তো তিন মাত্রার জ্যামিতিও করেছ। চার মাত্রার জ্যামিতি, স্বভাবতই, আরো একটু জটিল। ছবি - ৩: টান করে রাখা চাদরের ওপর ভারি একটা বস্তু রাখার ফলে চাদরের বিকৃতি, যেটা বোঝা যাচ্ছে কাটাকুটি লাইনগুলো বেঁকে যাওয়া থেকে। বস্তুটা যত ভারি হবে, বিকৃতি তত বেশি হবে। আবার বস্তুটা থেকে যত দূরে চলে যাব, বিকৃতিও কমে আসবে, আবার সমতল জ্যামিতি ফিরে পাব।আইনস্টাইন দেখিয়েছিলেন, কোনো জায়গার জ্যামিতি নির্ভর করে – সেখানে কী পরিমাণ বস্তু (বা শক্তি) আছে—তার ওপর। যদি কিছুই না থাকে, তাহলে জ্যামিতি হয় সমতল, টানটান করে পেতে রাখা একটা চাদরের মত। বস্তু থাকলে এই জ্যামিতিটা আর সমতল থাকে না, দুমড়ে যায়, যেমন টানটান করে রাখা চাদরের মধ্যে একটা ইট ফেললে সেখানে চাদরটা একটু নেমে যায়। বস্তু যত ভারি হয়, এই দোমড়ানো বা বিকৃতির পরিমাণ তত বেশি হয়, ৩ নং ছবি দেখো। দেশকালের এই বিকৃতিই মহাকর্ষের প্রভাব হিসেবে আমাদের কাছে ধরা দেয়। কতটা বস্তু থাকলে কীরকম বিকৃতি হবে, সেটাই সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের বা আধুনিক মহাকর্ষ তত্ত্বের মূল সমীকরণ, যাকে আইনস্টাইনের সমীকরণও বলা হয়। সমীকরণটি যথেষ্ট জটিল, আর সবক্ষেত্রে এর সমাধানও, অন্তত কম্পিউটার ব্যবহার না করে শুধু কাগজে কলমে—সম্ভব নয়। শুধু বলে রাখা উচিত, বিশেষ কিছু ক্ষেত্র ছাড়া নিউটনের তত্ত্ব ও আইনস্টাইনের তত্ত্ব থেকে পাওয়া ফল একদম অভিন্ন।আইনস্টাইন প্রথম যখন এই সমীকরণটি লেখেন, তখনো সকলের ধারণা ছিল মহাবিশ্ব স্থির, অর্থাৎ গ্যালাক্সিরা চিরকাল একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। মুশকিল হল, মহাবিশ্ব স্থির ধরে নিলে আইনস্টাইনের সমীকরণে একটা বড় ধরণের অসঙ্গতি থেকে যায়। সেটা কাটানোর জন্যে আইনস্টাইন করলেন কি—তিনি ওই জ্যামিতির হিসেবের মধ্যে হাতে করে আরো একটা জিনিস ঢুকিয়ে দিলেন—যার একমাত্র উদ্দেশ্য ওই অসঙ্গতিটা দূর করা। এই গা-জোয়ারি করে ঢোকানো জিনিসটার নাম তিনি দিলেন কসমোলজিক্যাল কনস্ট্যান্ট, আর একে গ্রিক অক্ষর Λ (বড় হাতের ল্যামডা) দিয়ে চিহ্নিত করলেন।মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই জ্যোতির্বিজ্ঞানী এডউইন হাবল্ দেখালেন, মহাবিশ্ব মোটেই স্থির নয়। বরং সব গ্যালাক্সি একে অন্যের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে – যে গ্যালাক্সি আমাদের থেকে যত দূরে আছে, তার সরে যাওয়ার বেগ তত বেশি। তার মানে এই নয়, যে, আমরা মহাবিশ্বের কেন্দ্রে আছি। ব্যাপারটা কীরকম জানো? মনে কর, একটা বেলুনের ওপর কয়েকটা ফুটকি কাটা আছে। এবার তুমি বেলুন যত ফোলাবে, প্রত্যেক ফুটকি একে অন্যের থেকে দূরে সরে যাবে। বিজ্ঞানীরা বললেন, মহাবিশ্বও এইরকম ফুলছে, তার ফলে গ্যালাক্সিরা একে অন্যের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। মহাবিশ্ব স্থির নয়, প্রসারণশীল। ছবি - ৪: মহাবিশ্বের প্রসারণ। সূত্র: Eugenio Bianchi, Carlo Rovelli & Rocky Kolbমহাবিশ্বের এই বেড়ে চলা হিসেবে নিলে একটা ম্যাজিকের মত ব্যাপার ঘটে। আইনস্টাইনের সমীকরণে ওই অসঙ্গতিটা আর থাকে না, তার ফলে Λ জিনিসটার আর কোনো প্রয়োজনও থাকে না। আইনস্টাইন বললেন, তাঁর নিজেরই নিজের সমীকরণের ওপর আরেকটু ভরসা থাকা উচিত ছিল, তাহলে তিনি নিজেই বলতে পারতেন মহাবিশ্ব স্থির থাকতে পারে না। বিজ্ঞানীরা Λ-কে নির্বাসন দিলেন। আইনস্টাইন বললেন, আমার হিমালয়প্রমাণ ভ্রান্তি। সত্যিই কি তাই? বোধহয় না, কিন্তু সেখানে যাবার জন্যে আমাদের আরো পঁচাত্তর বছর অপেক্ষা করতে হবে। তার আগে আরো একটা গল্প আছে।১৯৩৩ সালে ফ্রিৎজ জুইকি নামে এক বিজ্ঞানী দেখালেন, মোট পরমাণুর হিসেব থেকে ছায়াপথের ভর বের করতে গেলে একটা গোলমাল হচ্ছে। ছায়াপথের স্পাইরাল বাহুতে যে সমস্ত নক্ষত্র আছে, তারা সকলেই ছায়াপথের কেন্দ্রের চারদিকে আস্তে আস্তে ঘুরছে। ছায়াপথের দৃশ্যমান ভরের প্রায় পুরোটাই এই কেন্দ্র অঞ্চলে অবস্থিত (কেন্দ্রের গল্পটা সংক্ষেপে বলেছি শেষের দিকে। সেখানে যে ঠিক কী আছে, তা দেখানোর জন্যে এই বছর, ২০২০ সালে, রাইনহার্ট গেঞ্জেল এবং আন্দ্রেয়া গেজ নামে দুই বিজ্ঞানী নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন)। কিন্তু তাহলে ওই নক্ষত্রদের ঘোরার বেগ যত হওয়া উচিত, পাওয়া যাচ্ছে তার চেয়ে অনেক বেশি। জুইকি বললেন, এর একমাত্র ব্যাখ্যা মহাবিশ্বের সব ভরই দৃশ্যমান নয়। অনেকটা জিনিস আছে যা আমরা চোখে (অর্থাৎ যন্ত্রপাতি দিয়ে) দেখতে পাই না, শুধু তার মহাকর্ষীয় টান অনুভব করতে পারি। এর নাম দিলেন ডার্ক ম্যাটার বা কৃষ্ণবস্তু।কৃষ্ণ কেন? আমরা যা দেখি, সবই কোনো না কোনো রকম আলো দিয়ে দেখি, সে রেডিও তরঙ্গ বা গামারশ্মি যাই হোক না কেন। গাছের পাতার ওপর আলো পড়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে আমাদের চোখে এসে পৌঁছলে পাতাটাকে দেখতে পাই। কৃষ্ণবস্তু হল অন্ধের চোখের মত, সেখানে আলো কোনো সাড়া ফেলে না, তাই আলো দিয়ে তাকে দেখা যায় না। কিন্তু তার ভর আছে বলে মহাকর্ষীয় টান অনুভব করা যায়। তার মানে, কৃষ্ণবস্তু মোটেই সাধারণ পরমাণু দিয়ে তৈরি নয়। কী দিয়ে যে তৈরি, তা এখনো আমরা জানি না—বিজ্ঞানীরা জানার চেষ্টা চালাচ্ছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বেশ কিছু গবেষণাগার কৃষ্ণবস্তুর চিহ্ন ধরার পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে। যেটুকু জানি, তা এই যে আমাদের গ্রহ তারা মহাজাগতিক মেঘ গ্যালাক্সি নিয়ে এই দৃশ্যমান জগৎ কৃষ্ণবস্তুর সমুদ্রে ডুবে আছে। মহাবিশ্বে কৃষ্ণবস্তুর মোট ভর দৃশ্যমান ভরের প্রায় পাঁচ গুণ। অর্থাৎ, বেশিটাই অজানা।কী অদ্ভুত, তাই না? কৃষ্ণবস্তু যে কোথা থেকে এলো, কী দিয়ে তৈরি, কিছুই আমরা জানি না। শুধু তারা যে মহাকর্ষীয় বলের নিয়ম মেনে চলে, সেটুকু জানি। গল্পের এখানেও শেষ নয়। এর চেয়েও অদ্ভুত জিনিস আছে।এডউইন হাবলের কথা বলছিলাম। তিনি দেখিয়েছিলেন, গ্যালাক্সিরা একে অন্যের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। কোনো গ্যালাক্সি আমাদের থেকে যত দূরে আছে, তার সরে যাওয়ার বেগ সেই দূরত্বের সঙ্গে সমানুপাতিক। গ্যালাক্সি থেকে যে আলো আসে, তার বর্ণালী বিশ্লেষণ করে সরে যাওয়ার বেগ মাপা যায়। তোমরা অনেকে হয়তো ডপলার ক্রিয়ার কথা পড়েছ, মূল নীতি সেই ডপলার ক্রিয়া। এখন যন্ত্রপাতি অনেক উন্নত হয়েছে, মাপার নতুন নতুন পদ্ধতি বেরিয়েছে, ফলে হাবল যতদূর পর্যন্ত দেখতে পেয়েছিলেন, আমরা তার চেয়ে বহু বহুগুণ বেশি দূর পর্যন্ত দেখতে পাই। অতিদূরের এইসব গ্যালাক্সির বেগ মাপতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা একটা ধাক্কা খেলেন।আগে বলেছি, প্রায় চোদ্দশো কোটি বছর আগে এক মহাবিস্ফোরণে মহাবিশ্বের সৃষ্টি। সেই বিস্ফোরণের ধাক্কায় সব কিছুই একে অন্যের থেকে দূরে ছিটকে পড়েছিল, ছিটকে যাবার সে দৌড় এখনো চলছে। কিন্তু দৌড়ের বেগ কমে আসতে বাধ্য, কারণ মহাকর্ষের টান। বেগ কতটা কমবে, তা নির্ভর করে মহাবিশ্বে মোট কতটা ভর (এবং শক্তি) আছে তার ওপরে। প্রায় পঁচিশ বছর আগে দু-দল বিজ্ঞানী দেখলেন, বহুদূরের (কয়েকশো থেকে কয়েক হাজার মেগাপার্সেক পর্যন্ত) গ্যালাক্সিগুলোর দৌড়ের বেগ কমছে তো না-ই, বরং আরো যেন বেড়ে যাচ্ছে। যেন কেউ তাদের আরো জোরে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে।এরকম তো হবার কথা ছিল না? মহাকর্ষ বল আকর্ষক, দুটো বস্তুকে একে অন্যের দিকে টেনে আনে, বিকর্ষণ তো ঘটায় না? তার মানে, এখানে কি অন্য কোনো একটা বল কাজ করছে? ঠিক কি যে হচ্ছে বোঝা না গেলেও, বিকর্ষণ যে ঘটছে এ বিষয়ে দু-দল বিজ্ঞানীই নিঃসন্দেহ হলেন। এটা সম্পূর্ণ অভাবনীয়, আমাদের সব প্রচলিত ভাবনাচিন্তার বাইরে। কিন্তু সেটাই তো বিজ্ঞানের মজা। এই আবিষ্কারের জন্যে ২০১১ সালে এঁরা নোবেল পুরস্কার পান।যা বোঝা গেল, মহাবিশ্বে এক অদ্ভুত রকমের শক্তির ভাণ্ডার আছে, সেই শক্তিই গ্যালাক্সিদের বেশি জোরে দূরে ঠেলে দিচ্ছে। এই শক্তি কোথা থেকে এল, কী এর উৎস, এর ধর্মই বা কী, কিছুরই স্পষ্ট কোনো উত্তর এখনো পাওয়া যায়নি। বিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছেন ডার্ক এনার্জি বা কৃষ্ণশক্তি (কৃষ্ণবস্তুর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই কিন্তু)।মহাবিশ্বের মোট ভর ও শক্তির তাহলে তিনটে অংশ হল। এক, দৃশ্যমান, বিভিন্ন অণু-পরমাণু, আলো, এই সব মিলিয়ে। দুই, কৃষ্ণবস্তু, যার মহাকর্ষের টান আছে, কিন্তু সাধারণ অণু-পরমাণু দিয়ে তৈরি নয়। তিন, কৃষ্ণশক্তি, যা শুধু আছে বলে জানি, তার চেয়ে বেশি কিছুই প্রায় জানি না। এখন মোট ভর ও শক্তির প্রায় ৫ শতাংশ দৃশ্যমান, প্রায় ২৫ শতাংশ কৃষ্ণবস্তু, আর প্রায় ৭০ শতাংশ কৃষ্ণশক্তি! ভেবে দেখ, মহাবিশ্বের ৯৫ শতাংশই কী দিয়ে তৈরি, সে সম্বন্ধে আমাদের কোনো ধারণাই নেই।মহাবিশ্ব যখন তার যাত্রা শুরু করেছিল, তখন কিন্তু প্রায় পুরোটাই ছিল দৃশ্যমান বস্তু ও কৃষ্ণবস্তু, কৃষ্ণশক্তির অস্তিত্ব প্রায় ছিলই না। যত দিন যাচ্ছে, কৃষ্ণশক্তির পরিমাণ বাড়ছে, আরো কয়েকশো কোটি বছর পরে কৃষ্ণশক্তিই মহাবিশ্বকে পুরো কব্জা করে নেবে, আর তার প্রসারণের বেগও হু হু করে বেড়ে চলবে। আমরা কেউই অবশ্য সে সব দিন দেখার জন্যে থাকব না।কৃষ্ণশক্তি যে কী—সেটা আমরা জানি না, কিন্তু আমাদের চেনা একটা জিনিস আছে যেখান থেকে কৃষ্ণশক্তি আসতে পারে। সে হল বহুকাল আগে ফেলে দেওয়া আইনস্টাইনের সেই হিমালয়প্রমাণ ভ্রান্তি, কসমোলজিক্যাল কনস্ট্যান্ট Λ, যার কথা প্রায় পঁচাত্তর বছর বিজ্ঞানীদের মনেই পড়েনি। দেখানো যায়, যে Λ যদি শূন্য না হয়, তাহলে মহাবিশ্বের এইরকম অদ্ভুত প্রসারণ সম্ভব। এই ব্যাখ্যাটার মধ্যেও কিছু অসঙ্গতি আছে (নইলে তো বলতামই যে কৃষ্ণশক্তি কী আমরা বুঝে ফেলেছি), কিন্তু আপাতত এর চেয়ে ভালো ব্যাখ্যা আমাদের হাতে আর নেই। শেষ যে জিনিসটার কথা বলব, তার নাম তোমরা অনেকেই শুনেছ, হয়তো কাগজে বা টিভিতে ছবিও দেখেছ। এর নাম ব্ল্যাক হোল বা কৃষ্ণগহ্বর। নামে মিল থাকলেও এটা অত রহস্যময় কিছু নয়, অন্তত এর বিজ্ঞান আমরা অনেকটাই জানি।আইনস্টাইনের সমীকরণের কথা আগে বলেছি। প্রথম যে সব বিজ্ঞানী এর সমাধান করেছিলেন, তাঁদের একজন হলেন কার্ল শোয়ার্ৎসশিল্ট। একটা ফুটবলের মত গোল ভর স্থির রেখে দিলে তার চারপাশে জ্যামিতি কতটা বিকৃত হবে, সেটা তিনি হিসেব করে দেখিয়েছিলেন। তাঁর হিসেব মত, এই গোলকটার ঘনত্ব যত বাড়বে, বিকৃতিও তত বাড়তে থাকবে। অর্থাৎ, পৃথিবীর ভর ঠিক রেখে যদি কেউ তাকে চেপে ছোট করে দিতে পারত, তাহলে পৃথিবীর চারপাশে জ্যামিতির বিকৃতিও বেড়ে যেত। আরেকটু সোজা ভাষায় বললে, অভিকর্ষজ ত্বরণের মান বেড়ে যেত। ভর ঠিক রেখে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ কমালে যে অভিকর্ষজ ত্বরণের মান বাড়বে, এটা তো তোমরা সবাই জানো। এখন পৃথিবীর টান কাটাতে হলে কোনো জিনিসকে সেকেন্ডে প্রায় ১১ কিলোমিটার গতিতে ছুঁড়তে হয়, তখন আরও অনেক বেশি গতিতে ছুঁড়তে হবে। তাহলে এবার একটা প্রশ্ন করাই যায় – পৃথিবীকে চেপে কি এত ছোট করে দেওয়া সম্ভব, যে আলোও বেরিয়ে যেতে পারবে না? আলোর বেগ মহাশূন্যে সেকেন্ডে প্রায় তিন লক্ষ কিলোমিটার, এর চেয়ে বেশি বেগে কেউই ছুটতে পারে না, সুতরাং আলো না বেরোতে পারলে আর কারও পক্ষেই বেরোনো সম্ভব নয়। এর উত্তর হল, হ্যাঁ; পৃথিবীর ব্যাসার্ধ যদি একটা মার্বেলের গুলির মত করে দেওয়া যেত, সবটুকু ভর অটুট রেখে, তাহলে সেই বামন পৃথিবীর থেকে আলোও বেরোতে পারতো না।সেই পৃথিবীকে কি আমরা দেখতে পেতাম, মঙ্গল বা বৃহস্পতি, বা আরও দূরের কোথাও বসে? পেতাম না, কারণ আলো দিয়েই তো দেখি, আলো যদি না বেরোতে পারে, তাহলে সেই অদ্ভুত জিনিসের খবর কে নিয়ে আসবে? শুধু একটা চিহ্ন রয়ে যাবে – ঐ বিরাট ঘনত্বের ফলে বাইরের জ্যামিতি দুমড়ে মুচড়ে একাকার হয়ে যাওয়া। একেই বলে কৃষ্ণগহ্বর বা ব্ল্যাক হোল।এটা খুব কষ্টকল্পনার মত শোনাচ্ছে, কিন্তু শোয়ার্ৎসশিল্ট দেখিয়েছিলেন, যে আইনস্টাইন সমীকরণের সত্যিই এরকম একটা সমাধান সম্ভব, যেখানে দেশকালের বিকৃতি অসীম হয়ে যেতে পারে। দেশকালের জ্যামিতিতে সেরকম বিন্দুর অস্তিত্ব আমরা কেউই চাই না, কারণ প্রকৃতিতে তো আর অসীম বলে কিছু হয় না, কিন্তু অঙ্ক বলছে এরকম বিন্দু থাকতে পারে। এদের বলে ব্যতিক্রমী বিন্দু বা সিংগুলারিটি, y=1/x সমীকরণ সমাধান করে x=0 বিন্দুতে y-এর মান বের করতে গেলে যেরকম হবে আর কি। ভাগ্যক্রমে, এই ব্যতিক্রমী বিন্দু আমরা দেখতে পাই না, কারণ তা থাকে এক অদৃশ্য আবরণের পেছনে। ছবি - ৫: M-৮৭ গ্যালাক্সির কেন্দ্রে অবস্থিত কৃষ্ণগহ্বর। বাইরে থেকে যে সব বস্তু কৃষ্ণগহ্বরে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, তাদের বিকীর্ণ আলোর বলয় দেখা যাচ্ছে ইভেন্ট হরাইজনের বাইরে। এই কৃষ্ণগহ্বরটি নিজের অক্ষের চারদিকে পাক খাচ্ছে বলে আলোকবলয় সর্বত্র সমান উজ্জ্বল নয়। (সূত্র: EHT Collaboration)এই আবরণটিকে বলে ইভেন্ট হরাইজন। কোনো বস্তু যতক্ষণ ইভেন্ট হরাইজন পার করেনি, ততক্ষণই তার থেকে আলো এসে আমাদের কাছে পৌঁছতে পারে, একবার ইভেন্ট হরাইজন পেরিয়ে গেলে আলোরও সাধ্য নেই সেই ভয়ঙ্কর আকর্ষণ কাটিয়ে বেরোয়। কৃষ্ণগহ্বর থাকে এই ইভেন্ট হরাইজনের ভেতরে, ব্যতিক্রমী বিন্দু সমেত, সুতরাং কৃষ্ণগহ্বরের সাইজ কীরকম সে আমরা কোনোদিনই জানতে পারব না, একমাত্র ইভেন্ট হরাইজনের সাইজ জানা সম্ভব। তোমরা কৃষ্ণগহ্বরের যে ছবি দেখেছ (৪ নং ছবি), একটা গোল কালো বৃত্তের মত, ঐটাই ইভেন্ট হরাইজন।আইনস্টাইনের সমীকরণে ব্যতিক্রমী বিন্দুর অস্তিত্ব কি অবধারিত? আইনস্টাইনের মৃত্যুর এক মাসের মধ্যে, ১৯৫৫ সালে, এই বিষয়ে বিজ্ঞানের বিখ্যাত পত্রিকা ফিজিক্যাল রিভিউ-তে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ব্যতিক্রমী বিন্দু বিষয়ে যাবতীয় গবেষণার ভিত্তিপ্রস্তর হিসেবে এই প্রবন্ধটিকে ধরা যেতে পারে। এর লেখক সদ্য ত্রিশোর্ধ্ব এক বাঙালি বৈজ্ঞানিক, পরবর্তী জীবনে প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রবাদপ্রতিম অধ্যাপক অমলকুমার রায়চৌধুরী। এই কাজটিকে আমি ব্যক্তিগতভাবে স্বাধীন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ তাত্ত্বিক গবেষণা বলে মনে করি। অমলকুমার দেখান, যে দেশকালের মধ্যে দিয়ে কোনো বস্তুকণার গতিপথ যদি আমরা অনুসরণ করি, তাহলে ব্যতিক্রমী বিন্দুর দেখা পাওয়া উচিত। মনে রাখতে হবে, অমলকুমার কৃষ্ণগহ্বর সম্বন্ধে কিছু বলেননি, তাঁর আলোচনার কেন্দ্রে ছিল মহাবিশ্বতত্ত্ব বা কসমোলজি। বস্তুকণার গতিপথের এই সমীকরণটি রায়চৌধুরি সমীকরণ নামে পরিচিত। দশ বছর পরে এই কাজটিকেই আরো অনেক এগিয়ে নিয়ে যান রজার পেনরোজ (যিনি এ বছর [২০২০] নোবেল পেয়েছেন), এবং স্টিফেন হকিং। বেশিরভাগ গ্যালাক্সির কেন্দ্রে অতি বিশাল এক কৃষ্ণগহ্বর আছে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন। M87 গ্যালাক্সির কেন্দ্রের কৃষ্ণগহ্বরের ছবি কিছুদিন আগেই মিডিয়ার কল্যাণে সকলের কাছে পৌঁছেছিল (ছবি-৪)। আমাদের ছায়াপথ গ্যালাক্সির কেন্দ্র আকাশে ধনুরাশি বা স্যাজিটারিয়াস নক্ষত্রমণ্ডলীর দিকে। এখানেও এরকম সুবিশাল এক কৃষ্ণগহ্বর আছে বলে বিজ্ঞানীরা অনুমান করতেন। কৃষ্ণগহ্বর থেকে তো আর আলো বেরোয় না, কিন্তু আশপাশের তারা থেকে কৃষ্ণগহ্বর যখন তার মহাকর্ষের টানে জিনিসপত্র লুঠ করতে থাকে, সেই লুঠ হওয়া জিনিসপত্র কৃষ্ণগহ্বরে মিলিয়ে যাবার আগে আলোর চিহ্ন পাঠিয়ে যায়। মুশকিল হল, পৃথিবীতে বসে সেই আলো দেখাও ভারি শক্ত, কারণ ছায়াপথের কেন্দ্র আর আমাদের মধ্যে আছে বিশাল মহাজাগতিক ধূলিকণা ও গ্যাসের মেঘ, তারা প্রায় সব আলোটুকুই শুষে নেয়।আর একটা রাস্তা আছে, এই কৃষ্ণগহ্বরকে কেন্দ্র করে যে তারাগুলো পাক খায়, তাদের আবর্তনকাল মেপে কেপলারের সূত্রের সাহায্যে কৃষ্ণগহ্বরের ভর নির্ণয় করা। এটাও যথেষ্ট কঠিন কাজ, কিন্তু বিজ্ঞানীরা সফলভাবেই করেছেন। এই রকম দুটি পর্যবেক্ষক দলের নেতৃত্ব দিয়েছেন এ বছর পেনরোজের সঙ্গে নোবেল পুরস্কার ভাগ করে নেওয়া রাইনহার্ট গেঞ্জেল ও আন্দ্রেয়া গেজ। মনে রেখো, নোবেল পুরস্কারের ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণের একটা বড় ভূমিকা আছে, শুধুমাত্র তত্ত্বের ভিত্তিতে নোবেল দেওয়া হয় না—আইনস্টাইনও তাঁর মহাকর্ষের তত্ত্বের জন্যে নোবেল পাননি।বিজ্ঞানীরা মাপজোখ করে যা পেয়েছেন, তা সংক্ষেপে এইরকম – ছায়াপথের কেন্দ্রে যে বস্তুটি আছে (এর পোশাকি নাম Sagittarius A*), তার ভর সূর্যের ভরের প্রায় ছত্রিশ লক্ষ গুণ, কিন্তু ব্যাস মাত্র ছ-কোটি কিলোমিটার (পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব প্রায় পনেরো কোটি কিলোমিটার)। পুরোটা যদি কৃষ্ণগহ্বর না-ও হয়, এর কেন্দ্রে যে এক দানব কৃষ্ণগহ্বর বসে আছে—অন্যান্য গ্যালাক্সির মতই—সে ব্যাপারে বিজ্ঞানীরা মোটামুটি নিশ্চিত। কিন্তু এ তো আমাদের নিজেদের ঘরের ব্যাপার, পৃথিবী থেকে এর দূরত্ব মাত্রই ছাব্বিশ হাজার আলোকবর্ষ, সুতরাং ভবিষ্যতে এর থেকে যে আরও অনেক চাঞ্চল্যকর খবর পাওয়া যাবে—গেঞ্জেল ও গেজের নোবেল পুরস্কার যেন আরেকবার সেটাই মনে করিয়ে দিল।আগামী কয়েক দশক, আশা করা যায়, মহাবিশ্ব সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানকে অনেকখানি এগিয়ে দেবে। ঠিক কোন পথে যে এগোবে, তা আমরা এখনো জানি না। যে কটা প্রশ্নের কথা এখানে বললাম, তার বাইরে আরো বহু প্রশ্ন আছে, এমনকি আমাদের প্রচলিত ধ্যানধারণা চুরমার হয়ে যেতে পারে, এমন সম্ভাবনাও আছে বৈকি। সেইজন্যেই তো গোড়াতেই বললাম, ভেবে দেখো—এই অ্যাডভেঞ্চারে যোগ দেবে কিনা।মারিয়াজ ক্রিয়েশন ও গুরুচন্ডা৯ - শুরু হোক পথ চলা - Maria’s Creation | গুরুতে আছি বহুদিন ধরে – কিন্তু ব্লগ লেখার কথা সেভাবে ভাবিনি কখনো। এখানে এত জ্ঞানীগুণী মানুষেরা লেখেন, মন্তব্য করেন, আমার সেসব পড়েই মন ভরে। শুনেছি গুরুর ভাষায় আমাদেরকে বলে নীপা – নীরব পাঠক। সেই হয়েই খুশী ছিলাম এতদিন – তাইই থাকতাম হয়তো, যদি না আমার নিজের কিছু কথা বলে ফেলা জরুরী হয়ে উঠত। পিছনে উৎসাহদাতার ভূমিকায় তো সে না বললেও চলে, ইপ্সিতাদি, ওয়ান অ্যান্ড ওনলি। যাই হোক, যে কথা বলব বলে এত ভূমিকা, সেই কথাতেই আসি এবার।কেরিয়ার, চাকরি ইত্যাদি করতে কোনোদিন ভালোবাসিনি। হয়তো সেরকম কিছু করে ওঠার ক্ষমতাও ছিল না, সে দুই একবার চেষ্টা করতে গিয়ে কিছুটা বুঝেছি। কিন্তু যেটা করতে ছোট থেকে ভালোবাসতাম, যেটা আমাকে আমার নিজস্ব জগতের খোঁজ দেয়, সেটাকে যে নিজের পেশা হিসাবেও নেওয়া যায়, এ কথা বুঝে উঠতেও খরচ হয়ে গেল অনেকগুলো বছর, জীবনের বহু অমূল্য সময়। অবশেষে বছর চারেক আগে থেকে শুরু হয়েছে সেই পথচলা – যা একটু একটু করে এখন একটা হাঁটি হাঁটি পা পা প্রতিষ্ঠানে এসে ঠেকেছে – মারিয়াজ ক্রিয়েশন। শুরু করেছিলাম আমি একাই, নিজের আঁকা, নিজের হাতে তৈরি ক্রাফট, এসব দিয়ে। সেই সঙ্গে ইন্টযিরিয়ার ডেকোরেশন – ঘর বা দোকান সাজানোর ছোট ছোট বরাত। এখনও ব্যাপারটা তাইই আছে, শুধু সঙ্গে জুটেছে কয়েকটি ছানাপোনা – যারা আমার এবং কখনো কখনো নিজেদের ভাবনা দিয়েও জিনিষপত্র বানাচ্ছে আমারই সঙ্গে বসে। রোজগারপাতি বিশাল কিছু হচ্ছে এমন না, কিন্তু কাজটা করছে তারা মনের আনন্দে। আমিও তাই।ইপ্সিতাদি বলেছিল, মারিয়া, তুই যখন করছিসই, আমাদের থিম তো আলাদা কিছু নয়, একসাথে কিছু করার কথা ভাব না। তো সেই ভাবনা থেকেই গাঁটছড়া হল গুরুচণ্ডা৯র সাথেও – যে গুরুচণ্ডা৯ আমার আরেক ভালোলাগার জায়গা, যেখানে এসে আমি প্রাণভরে নিশ্বাস নিই। এ বছর বইমেলায় গুরুচণ্ডা৯র স্টলে ছিল মারিয়াজ ক্রিয়েশনের বেশ কিছু সৃষ্টি, স্টলসজ্জা এবং বিক্রি, দুইএর জন্যই। এই যৌথ উদ্যোগের পরবর্তী ধাপ হিসাবে তাই গুরুর পাতায় তুলে আনলাম আমার কিছু সৃষ্টি । আপনারা চাইলে নীচের হোয়াটস-অ্যাপ নম্বরে, মেইল আই ডি তে বা গুরুচণ্ডা৯ র পাতার মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারেন 'গুরুচণ্ডা৯-মারিয়াজ ক্রিয়েশনে'র জিনিষপত্র কিনতে চাইলে। কেউ যদি ইন্টিরিয়ার ডেকোরেশনে আগ্রহী হন, তাহলেও যোগাযোগের পন্থা থাকবে একই। এখানে আমাদের কিছু প্রোডাক্টের ছবি মন্তব্যের ঘরে রাখা থাকল। পরবর্তীতে পাবেন আরও ছবিছাবা, যেমন আসে গুরুতে। আর ওই যেমন বলে, দেখাশোনা ফ্রী, কেনাকাটা ব্যক্তিগত ব্যাপার।যোগাযোগের জন্য -ফোনঃ- ৮৪৭৯০৬০৭৮৬হোয়াটসঅ্যাপঃ ৮৪৭৯০৬০৭৮৬ই মেইলঃ- [email protected]ঠিকানাঃ-২৯/১ বিদ্যাসাগর সরণি, ডাক্তার বাগান। কলকাতা - ৭০০০৭৮কিষেণজি মৃত্যু রহস্য - পর্ব ৭ - বিতনু চট্টোপাধ্যায় | কলকাতার কিড স্ট্রিটে এমএলএ হস্টেলে এক বিধায়কের ঘরে বসে কথা কথা হচ্ছিল সিপিআইএম নেতা ডহর সেনের সঙ্গে। জিজ্ঞেস করলাম, ‘আপনার দলের বাড়াবাড়ির কথা বলছিলেন। কেন তা শুরু করতে হল? আপনারা রাজনৈতিকভাবে কেন মোকাবিলা করতে পারলেন না ঝাড়খন্ড পার্টির?’ ফের প্রশ্ন করলাম ডহর সেনকে।‘দেখুন সশস্ত্র মোকাবিলাটা শুরু হল আটের দশকের মাঝামাঝি কিংবা শেষ দিক থেকেই। নরেন হাঁসদা এমএলএ হওয়ার পর থেকে বিনপুর, বেলপাহাড়িতে ঝাড়খন্ডিদের প্রভাব বাড়াতে শুরু করে। গরিব আদিবাসীদের মধ্যে ওদের সমর্থন ছিলই, তা আরও বেড়ে যায়। এই এলাকাগুলোতে সাংগঠনিকভাবে আমরা দুর্বল হয়ে পড়ি। সেই সময় বহুবার হয়েছে, আমরা বেলপাহাড়ি, বিনপুরে কোনও কর্মসূচিতে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছি। ঝাড়খন্ড পার্টির তখন একমাত্র স্লোগান ছিল, সিপিআইএমকে এলাকায় ঢুকতে দেওয়া হবে না। একবার সুকুমার সেনগুপ্তর সঙ্গে আমরা বিনপুর যাচ্ছি। দহিজুড়ি থেকে কিছু কর্মী-সমর্থককে নিয়ে লরিতে চেপে। কিছুটা যেতেই ঝাড়খন্ডিরা আমাদের লরিতে তীর, ধনুক নিয়ে আক্রমণ করল। আমাদের এক কর্মী তীর বিদ্ধ হয়ে মারাই গেল। তার কয়েক মাস বাদে ভেলাইডিহা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় আমাদের ছ’জন যুব নেতাকে খুন করল ঝাড়খন্ডিরা। সেই সময় থেকেই আমাদের বহু কর্মী, সমর্থক ঝাড়খন্ডিদের মোকাবিলায় অস্ত্র হাতে নিল। আর সেই যে অস্ত্রের লড়াই শুরু হল তা থামল গিয়ে একদম রাজ্যে সরকার থাকা পর্যন্ত।’‘কিন্তু এই লড়াই-পাল্টা লড়ায়ের শেষ কোথায়? এই যে গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে একটা সিভিল ওয়ার টাইপ সিচুয়েশন, এর পরিণতি কী হতে পারে তা নিয়ে কখনও আলোচনা হয়নি জেলা পার্টিতে?’‘দেখুন সেই সময় জেলা পার্টিতে আলোচনা কিংবা বিতর্কের পরিবেশ খুব একটা ছিল না। তবে, নেতাদের একটা বড় অংশের বক্তব্য ছিল, ঝাড়খন্ডিদের সশস্ত্রভাবেই মোকাবিলা করতে হবে। কারণ, ওদের অস্ত্রের সামনে বেলপাহাড়ি, বিনপুর, জামবনির বিভিন্ন এলাকায় পার্টি কর্মীরা ঘরছাড়া হচ্ছে। পার্টি অ্যাক্টিভিটি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বহু গ্রামে পার্টি নেতারা ঢুকতেই পারছেন না। তাই সশস্ত্র মোকাবিলা ছাড়া উপায় নেই। এবং এই অংশের বক্তব্যই পার্টিতে গৃহিত হল।’ আপাত দৃষ্টিতে দেখলে, অস্ত্রের বিরুদ্ধে অস্ত্রের লড়াই, এ তো দুনিয়ার ইতিহাসে নতুন কোনও তত্ত্ব নয়। তাছাড়া মানুষের আত্মরক্ষার অধিকার সংবিধান স্বীকৃতও বটে। কিন্তু ঝাড়গ্রাম মহকুমায় ঝাড়খন্ড পার্টির সঙ্গে সিপিআইএমের লড়াই, সংঘর্ষের মৌলিক প্রশ্নটা ছিল ভিন্ন। বিচ্ছিন্নভাবে কোনও ব্যক্তি থেকে শুরু করে যে কোনও সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আধার তার অর্থনৈতিক অবস্থান, তার শ্রেণি চরিত্র। এবং নিঃসংশয়ভাবে বলা যায়, ঝাড়গ্রামের যে দু’দল মানুষ আটের দশকের মাঝামাঝি থেকে রাজনৈতিক এলাকা দখলে অস্ত্র প্রতিযোগিতায় নামল, তাদের অর্থনৈতিক অবস্থান ছিল একই বিন্দুতে দাঁড়িয়ে। এও এক আশ্চর্য পরিস্থিতি যে, দু’দলের জাতিগত ভিত্তিও মূলত এক। ঝাড়গ্রাম মহকুমাজুড়ে এক দল গরিব আদিবাসী মানুষ আর এক দল গরিব আদিবাসীর বিরুদ্ধে নির্মম, রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ে নামল। এক দলের বাড়িতে দু’বেলা খাবার নেই, আর এক দলের বাড়ির হাঁড়িরও এক হাল। পক্ষ এবং প্রতিপক্ষ দু’দলের বাড়িতেই তখন চরম দারিদ্র। দু’দল মানুষই এক ভাষায় কথা বলে। অভিন্ন তাদের সংস্কৃতি। তাও শুরু হল তীব্র সংঘর্ষ। খুন-পালটা খুন। রক্তাক্ত হল অবিভক্ত মেদিনীপুরের একটা বিস্তীর্ণ এলাকা। আদিবাসীদের স্বল্প জীবন আরও ছোট হল। এই রাজনৈতিক লড়াইয়ে এক দলের পক্ষে আর এক দলের বিরুদ্ধে কি কোনও শ্রেণিগত স্লোগান দেওয়া সম্ভব ছিল? এক কথায় এর উত্তর, না। আটের দশকের মাঝামাঝি থেকে পশ্চিমবঙ্গের ঝাড়গ্রাম মহকুমায় কোনও শ্রেণি আন্দোলন সংগঠিত হচ্ছিল না।২০০৬ সালের পর থেকে ২০১১ পর্যন্ত বহুবার বেলপাহাড়ি, জামবনি, বিনপুর, লালগড়ে গিয়ে একটা প্রশ্নই শুধু মনে এসেছে। তা হল, যারা খুন করছে, আর যারা খুন হচ্ছে দু’দলই হত-দরিদ্র মানুষ। গরিব মানুষকে খুন করে গরিব মানুষ কোন শ্রেণি সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে এই আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায়? গরিব মানুষ জোতদারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরে বুঝি, কিন্তু আরও গরিব একজনকে খুন করে কোন উন্নততর সমাজ গড়ার স্বপ্ন দেখে, এই প্রশ্নের মীমাংসা না হলে, জঙ্গলমহলে সিপিআইএমের বামপন্থার অনুশীলনের মতোই কিষেণজির সংগ্রামও ব্যর্থ হতে বাধ্য, বারবার ভেবেছি এ কথা৷ আমি সব সময়ই বিশ্বাস করেছি, দায়িত্ববোধ এবং সহনশীলতা দুর্বলের থেকে শক্তিশালীর, সংখ্যালঘুর থেকে সংখ্যাগুরুর এবং বিরোধীর থেকে শাসকের বেশি হওয়া উচিত। তবেই সমাজে ভারসাম্য বজায় থাকে। নয়তো সমাজের স্বাভাবিক ন্যায্যতা বিঘ্নিত হয়। দুর্বল, সংখ্যালঘু এবং বিরোধী নিজেকে বঞ্চিত মনে করে। মনে করে, তারা দুর্বল, সংখ্যালঘু এবং বিরোধী বলেই তাদের সঙ্গে জাস্টিস হচ্ছে না। এবং সেখান থেকে শুরু হয় সংঘাতের। এই সংঘাত সব সময় যে অর্থনৈতিক কারণে হয়, তা নয়। আর এই ঘটনাই ঘটল আদিবাসী অধ্যুষিত ঝাড়গ্রাম মহকুমার বিভিন্ন এলাকায়। আটের দশকে যে মুহূর্তে অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার সিপিআইএম নেতৃত্ব সিদ্ধান্ত নিল ঝাড়খন্ডিদের মোকাবিলায় সশস্ত্র রাস্তায় হাঁটার, সেদিনই সেই রাস্তার অন্য প্রান্তে ল্যান্ড মাইন পাতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে ফেলল মাওবাদীরা। সেই দিনই ঠিক হয়ে গিয়েছিল, সেই রাস্তার কোনও এক প্রান্তে একটা ছোট্ট গ্রাম খবরের শিরোনামে চলে আসবে অনেক বছর পর, ২০১১ সালের গোঁড়ায়। ঘটনাচক্রে সেই গ্রামের নাম হবে নেতাই। এই গ্রামের নাম হয়তো অন্য কিছু হতে পারত, কিন্তু ঘটনাটা ঘটতই। যেখানে সিপিআইএম নেতার বাড়ি থেকে শাসক দলের সশস্ত্র ক্যাডারদের ছোঁড়া গুলিতে মৃত্যু হবে একাধিক গ্রামবাসীর। গ্রামবাসীদের কিছু করারও থাকবে না, কারণ, মাওবাদীদের কথায় তারা সিপিএম ক্যাডারদের বাড়িতে বিক্ষোভ দেখাতে বাধ্য হবে! সেদিনই ঠিক হয়ে গিয়েছিল, এই জঙ্গলমহলের গ্রামের পর গ্রামে আপামর গরিব মানুষ ঝাড়খন্ড পার্টি, কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস, বিজেপি কিংবা অতিবাম মাওবাদীদের মধ্যে কোনও বাছবিচার না করে একদিন একই ছাতার তলায় এসে আশ্রয় নেবে শুধু সিপিআইএমের বিরোধিতা করার জন্য। আর সেই সম্মিলিত বিরোধিতা সামাল দেওয়ার কোনও রাস্তা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্ক্সবাদীর নেতাদের জানা থাকবে না একুশ শতকের প্রথম দশকে পৌঁছে। ঝাড়খন্ড পার্টির নেতা নরেন হাঁসদা বিধায়ক হওয়ার পরই এই সব এলাকায় রাজনৈতিক সংঘর্ষ তীব্র আকার ধারণ করে। সেই সময়ও ঝাড়খন্ড পার্টির প্রবল আক্রমণের মুখে দাঁড়িয়ে ডহর সেন পার্টিতে বলেছিলেন, ‘পালটা মারের লাইনে গিয়ে আদিবাসী ঝাড়খন্ডিদের সমর্থন পাওয়া যাবে না। ওদের উইন ওভার করতে হবে। ঝাড়খন্ড পার্টির অনুগামীরা বেশিরভাগই গরিব। আদিবাসী গ্রামগুলো বেশিরভাগই মোড়লদের কথায় চলে। মোড়লদের সঙ্গে কথা বলে তাদের কনফিডেন্সে নিতে হবে। গ্রামে থাকতে হবে আদিবাসীদের মতো করে। তবেই ওদের সমর্থন পাওয়া যাবে।’ বিনপুরে ঝাড়খন্ড পার্টির এক নেতা ছিলেন নয়ের দশকে, লিয়াকত আলি। এলাকায় পরিচিত ছিলেন হাত কাটা লিয়াকত নামে। সিপিআইএমের সঙ্গে বহু লড়াইয়ে ঝাড়খন্ডিদের নেতৃত্ব দিয়েছেন। এই লিয়াকত আলির সঙ্গে একাধিকবার কথাও বলেন ডহর সেন। কিন্তু তাঁর এই উদ্যোগ পার্টির মধ্যেই একাধিক নেতা ভাল চোখে দেখলেন না। আদিবাসী ঝাড়খন্ডিদের সঙ্গে দৌত্য করতে গিয়ে নিজের দলে একঘরে হয়ে গেলেন ডহরেশ্বর সেন। বেলপাহাড়ি, বিনপুর, জামবনির জঙ্গলমহলে সিপিআইএমের মুখ হিসেবে তখন দ্রুত উঠে আসছেন বাসুদেব ভকত। বাড়ি জামবনিতে। এই বাসুদেব ভকতের সঙ্গে কেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার প্রদীপ চট্টোপাধ্যায় কথা বলেন না, তা নিয়ে তাঁকে ফোনে হুমকি দিয়েছিলেন মেদিনীপুর জেলার সিপিআইএম সম্পাদক দীপক সরকার। কেন, কীভাবে বাসুদেব ভকত জঙ্গলমহলে সিপিআইএমের মুখ হয়ে উঠলেন, সে প্রসঙ্গে আসব একটু বাদেই। ডহর সেনের কাছে আর বিশেষ কিছু জানার ছিল না। শুধু জিজ্ঞেস করেছিলাম, ‘আত্মগোপনের সময় ১৯৬৬ সালে যে পুলিশ অফিসার আপনাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন, তার কারণ কিছু বুঝতে পেরেছিলেন?’‘না পারিনি। আমাকে তো চিনতেন না। সেদিনই প্রথম দেখা। হয়তো আমাদের দলের বক্তব্য সমর্থন করতেন, হয়তো আমাদের মনোভাবাপন্ন ছিলেন। জানি না ঠিক। তবে ওই অফিসারের নাম তুষার তালুকদার। ঝাড়গ্রামের প্রথম এসডিপিও।’ তুষার তালুকদার, এসডিপিও ঝাড়গ্রাম, ১৯৬৬তুষার তালুকদার যে শুধুমাত্র বামপন্থীদের প্রতিই সহমর্মী ছিলেন তা নয়, তিনি অত্যন্ত সংবেদনশীল ছিলেন গরিব প্রান্তিক মানুষের ছোট-বড় সমস্যা নিয়েও। আর তা হাড়ে হাড়ে বুঝেছিলেন ছোট্ট রামজীবনের বাবা মহাদেব মুর্মু। সিপিআইএম করা যুবক ডহরেশ্বর সেনকে নাগালে পেয়েও ছেড়ে দেওয়ার কয়েক মাসের মধ্যেই মহাদেব মুর্মুকে স্ত্রী খুনের অভিযোগ থেকে রেহাই দিয়েছিলেন তুষার তালুকদার। কম বয়সী নতুন এসডিপিও’র তখন ঝাড়গ্রাম মহকুমা মোটামুটি চেনা হয়ে গিয়েছে। তুষার তালুকদার চাকরি থেকে অবসর নেওয়ারও অনেক বছর বাদে, ২০১৫ সালে কথা বললাম তাঁর সঙ্গে। তাঁর দক্ষিণ কলকাতার ফ্ল্যাটে বসে। ঝাড়গ্রামের প্রথম এসডিপিও, কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার তুষার তালুকদার আমার পরবর্তী সাক্ষী। তাঁকে সাক্ষী বলা ঠিক হবে কিনা জানি না। ‘ঝাড়গ্রাম জায়গাটাকে আমার প্রথম দিনই খুব ভাল লেগে গিয়েছিল। প্রত্যেক অফিসারেরই চাকরি জীবনের শুরুতে যে সব জায়গায় পোস্টিং হয়, সেখানকার প্রতি একটা বাড়তি দুর্বলতা থাকে। অনেক স্মৃতি থাকে। আমারও ঝাড়গ্রাম নিয়ে আছে। সেটা নতুন কিছু নয়। কিন্তু ঝাড়গ্রামের যে জিনিসটা আমাকে নাড়া দিয়েছিল, তা হল সেখানকার মানুষের দারিদ্র্য। এত কষ্টের মধ্যেও মানুষ থাকে! যখন আমি গিয়েছিলাম, সেটা ছ’য়ের দশকের একেবারে মাঝামাঝি। চাষ-আবাদ কার্যত নেই। জলের প্রচণ্ড সমস্যা। স্কুল নেই, কলেজ নেই। গাড়ি করে পুরো মহকুমায় ঘুরে বেড়াতাম আর ভাবতাম, মানুষগুলো বেঁচে আছে কী করে?তখন ঝাড়গ্রামের সাংসদ কংগ্রেসের সুবোধ হাঁসদা। একদিন তাঁকে বললাম, ‘‘এই গরিব মানুষগুলোর জন্য কিছু করুন।’’‘‘চেষ্টা তো করছি, কিন্তু কী করা যায় বলুন তো?’’‘‘পুরো এলাকায় এত অনাহার আর অপুষ্টি। বেশিরভাগ লোক তো একবেলাও ঠিক করে খেতে পায় না। আগে ওদের খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে। রেশন দোকান তো চালায় সব বড়লোকরা। রেশনের চাল, ডাল পর্যন্ত গরিব মানুষের কাছে পৌঁছোচ্ছে না।’’‘‘আপনি তো সবই জানেন রেশন দোকানের মালিকদের দুর্নীতির কথা। আমি আর নতুন করে কী বলব?’’‘‘আমাদের দায়িত্ব দিন। পুলিশের মাধ্যমে রেশন বিলির ব্যবস্থা করুন। এটা আমাদের কাজ নয়। কিন্তু আমরা করব। রেশন সরবরাহে সরাসরি প্রশাসনকে যুক্ত না করলে প্রান্তিক, গরিব মানুষগুলো কোনওদিন ঠিক মতো চাল, ডাল পাবে না। রেশন মালিকরা বেআইনিভাবে চাল, ডাল মজুত করছে, আর গরিব আদিবাসী না খেতে পেয়ে মরছে। কোন দফতর দায়িত্ব নেবে জানি না, কিন্তু আমরা পুলিশ থেকে এই কাজ করতে রাজি আছি।’’‘‘এ হয় নাকি? কেন্দ্রীয় সরকার ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া মারফত রেশনে চাল, ডাল পাঠাচ্ছে। রাজ্যের পুলিশ কীভাবে তা বিলি করবে? আপনি আবেগ থেকে এ’কথা বলছেন।’’‘‘আবেগ থেকে বলছি না। যুক্তি থেকেই বলছি, যদিও যুক্তির পিছনে দেশের আইনের সমর্থন নেই। কিন্তু আইনের ওপরে সংবিধান। মানুষের খাবারের অধিকার নিশ্চিত করা সাংবিধানিক কর্তব্য।’’‘‘কিন্তু সারা দেশ এক আইনে চলছে। একটা মহকুমায় স্থানীয় স্তরে আপনি তা পাল্টাবেন কী করে? যদি গোটা দেশে এমন কিছু হয়, তবে সম্ভব। তার জন্য আইন পরিবর্তন করতে হবে। না হলে অন্তত কেন্দ্রীয় সরকার যদি বিশেষ কোনও অনুমতি দেয় তবে সম্ভব।’’‘‘আইন আগে না মানুষ আগে? আইনি বাধা যদি মানুষের জীবন রক্ষা করতে না পারে, তবে কোন আইন আপনারা রক্ষা করছেন? এই আইন রক্ষা করে লাভটাই বা কী? এই সব আইনি জটিলতায় তো মানুষগুলো মারা যাবে।’’ সাংসদ সুবোধ হাঁসদাকে সেদিন বোঝাতে পারিনি। কিন্তু নিজে বুঝতে পারছিলাম, এভাবে বেশিদিন চলবে না। সরকারি সাহায্য মানুষের কাছে প্রায় কিছুই পৌঁছচ্ছে না। তবে মানুষ সরকারকে মানবে কেন বেশিদিন? তাছাড়া এই দারিদ্র মানুষ কত দিন সহ্য করবে?’টানা বলে থামলেন তুষার তালুকদার। ঝাড়গ্রামের প্রথম এসডিপিওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ‘কিছুই করতে পারলেন না?’‘না, পারলাম না। এই শাসন ব্যবস্থাকে ভাঙতে হবে। নিয়ম-কানুন, আইন সব ভেঙে ফেলতে হবে। নয়তো সাধারণ মানুষের সামগ্রিক উপকার করা কঠিন।’রামজীবন মুর্মুর ডায়েরিএই লেখায় আমার চতুর্থ সাক্ষী রামজীবন মুর্মু। বলা যেতে পারে, কিষেণজি মৃত্যু রহস্যে এক গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী। যাঁর সঙ্গে আমার কথা শুরু হয়েছিল আগেই। আদিবাসী অধ্যুষিত ঝাড়গ্রাম মহকুমার সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক জীবন, তার নানান ওঠাপড়ার যে বহুমাত্রিক কাহিনী তাতে রামজীবন মুর্মু একটা প্রতীকি চরিত্র মাত্র। এমন হাজার-লক্ষ রামজীবন এবং তাঁর মতো পরিবার নিয়েই গড়ে উঠেছে জঙ্গলমহল। যে জঙ্গলমহলে প্রবল-পরাক্রান্ত শাসক দল সিপিআইমের সঙ্গে লাগাতার যুদ্ধে জড়িয়েছে প্রথমে ঝাড়খন্ড পার্টি, পরে মাওবাদীরা। যে যুদ্ধ প্রায় সিভিল ওয়ারের আকার নিয়েছিল একটা সময়ের পর। অথচ রামজীবনের কাছে গোটা জীবনটাই একটা যুদ্ধ। বেঁচে থাকার যুদ্ধ। সেই যে ছোট্ট বয়সে বাবার ধাক্কায় বাড়ির উঠোনে পড়ে গিয়ে মায়ের মৃত্যু, তারপর থেকেই শুরু হয়েছিল যুদ্ধটা। ২০০৯ সালে যখন তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলাম, তখনও যুদ্ধ জারি আছে। ‘মামা বাড়িতে চলে আসার কয়েক মাস বাদে মামা আমাকে ইস্কুলে ভর্তি করে দিল। আগে কোনওদিন ইস্কুল যাইনি। মামাদের কিছুটা জমি ছিল। ১৪ বিঘা মতো হবে। বাবা সকাল সকাল মামার সঙ্গে মাঠে চলে যেত কাজে। আমিও উঠে পড়তাম তাড়াতাড়ি। ছটা-সাড়ে ছটার মধ্যে। তারপর ছোটখাট কিছু কাজ করতাম বাড়ির। কোনওদিন গরুকে খড় দেওয়া, কোনওদিন ছাগল চরানো। এক আধদিন বই খুলে বসতাম। তারপর ভাত, খেয়ে স্কুলে যেতাম। বাড়ি থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার দূরে ছিল স্কুল। সাড়ে নটায় বেরোতাম বাড়ি থেকে। আস্তে আস্তে কয়েকজন বন্ধু হয়ে গেল। এক সঙ্গে চার-পাঁচজন মিলে স্কুলে যেতাম। বাড়ি ফিরতাম বিকেল চারটে নাগাদ। আর ফিরেই দৌড়াতাম মাঠে। ফুটবল খেলতে।মামারা আমাদের থেকে অনেক বড়লোক ছিল। দু’বেলা ভাত হোত বাড়িতে। আমরা তো একবেলা খেতাম। তাও পুরো বছর নয়। মামাদের বাড়িতে রাতে কেরোসিনের আলো জ্বলত। আমাদের বাড়িতে আলো ছিল না। ফুটবল খেলে ফিরে সন্ধেবেলা কোনওদিন পড়তেও বসেছি। কুপি জ্বেলে। কিছু পরেই মামি তাগাদা দিয়েছে, ‘‘তেল নাই। বাতি নিবা।’’মাঝখানে একবার থামালাম রামজীবনকে। জিজ্ঞেস করেছি, ‘গ্রামে কি সবার অবস্থা একই রকম ছিল সেই সময়? নাকি বড়লোকও ছিল কিছু?’‘প্রায় সবার অবস্থাই ছিল এক রকম। মামার ১৪ বিঘা জমি ছিল। চাষ হোত। ধান হোত একবার। তার জন্য মামা বাড়িতে সারা বছর ভাত হোত দুবেলা। এই যা। অন্য জিনিসের টানাটানি ছিল। টাকা-পয়সা ছিল না তেমন। আর গ্রামে বেশিরভাগ পরিবার তো মামাদের থেকেও গরিব ছিল। বেশিরভাগ বাড়িতেই দু’বেলা ভাত হোতও না তখন। আমাদের বাড়িতেই তো হোত না। মামাবাড়িতে গিয়েই প্রথম দু’বেলা ভাত খেয়েছি আমি আর বাবা। বড়লোক ছিল না কেউই। তখন যার বাড়িতে খাবারের তেমন অভাব ছিল না, গ্রামে সেই বড়লোক। আমাদের গ্রামে একটাই ঘর বড়লোক ছিল। দাসরা। ওদের বাড়িতে লাইসেন্স বন্দুক ছিল। রিনিউ করতে নিয়ে যেত বছরে একবার। দাসদের বাড়িতে অনেক রাত অবধি লন্ঠনের আলো জ্বলত। ও বাড়ির ছেলে-মেয়েদের বছরে তিন-চারবার নতুন জামা কেনা হোত শহর থেকে। বাকি সবার ঘরে অভাব ছিল। মাঠে তো চাষের কাজ ছিল না সারা বছর। যখন মাঠের কাজ থাকত না বাবা জঙ্গলে যেত কাঠ কাটতে। তারপর কাঠ মাথায় চাপিয়ে বিক্রি করতে যেত বাড়ি বাড়ি। স্কুল ছুটি থাকলে আমিও অনেকবার বাবার সাথে কাঠ নিয়ে গেছি। দু’জনে জ্বালানি কাঠ বিক্রি করেছি বিভিন্ন গ্রামে ঘুরে ঘুরে। ২৫-৩০ কিলো কাঠ মাথায় চাপিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বিক্রি করত বাবা। ৩০ কিলো জ্বালানি কাঠ বিক্রি হত এক টাকায়।’‘৩০ কিলো কাঠ এক টাকা? কারা কিনত কাঠ?’ চমকে উঠে জিজ্ঞেস করেছি। আবার একটা বিড়ি ধরালেন রামজীবন। সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লেন। তারপর আবার শুরু করলেন। ‘তখন লোকের হাতে টাকা কোথায়? জিনিসের দামই বা কী? বাবা সকালে চলে যেত জঙ্গলে কাঠ কাটতে। সারাদিনের কাটা কাঠ নিয়ে বিকেলে বাড়ি ফিরত। পরদিন সকালে তা বিক্রি করতে বেরতো। একদিনের কাঠ বিক্রির এক টাকা দিয়ে আমাদের দু’দিন চলে যেত প্রায়। আমাদের বাড়ি ছিল জঙ্গলের একদম ধারে। যে গ্রামে জঙ্গল ছিল না, সেখানকার লোক কাঠ কিনত। জ্বালানি পাবে কোথায়? আমাদের গ্রামেই তো কয়েকটা ঘরে শুধু কুপি, লণ্ঠন ছিল। কিন্তু কেরোসিন কোথায়?’২০০৯ সালের মাঝামাঝি, লোকসভা ভোটের একদিন আগে রামজীবনের কথা শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল, টাইম মেশিনে চেপে গেছি এক অজানা দুনিয়ায়। অথচ মাত্র ২৮-৩০ বছর আগের কথা। ১৯৭৮-৭৯ সাল। সবে সিপিআইএমের নেতৃত্বে বাম সরকার হয়েছে। ১৯৭৭ এর জুনে শপথ নিয়ে জ্যোতি বসু বললেন, ‘এই সরকার চলবে গ্রাম থেকে।’ রামজীবনের সঙ্গে কথা বলতে বলতে মনে হচ্ছিল, তখন তো এই গ্রামগুলোর মানুষেরই জীবন চলত না। তো গ্রাম থেকে সরকার চলবে কীভাবে? ১৯৪৭ থেকে ’৭৭, রাজ্যে প্রাক সিপিআইএম যুগের ৩০ বছরে কী গতিতে এগিয়েছে গ্রাম বাংলায় গরিব মানুষের জীবন যাত্রা, বিশেষ করে ঝাড়গ্রামের মতো পিছিয়ে পড়া একটা মহকুমায়, তার এক নির্মম ছবি তুষার তালুকদার দেখেছিলেন রামজীবনের মায়ের মৃত্যুর দিন তাদের বাড়ি গিয়ে। তুষার তালুকদারের ১৯৬৬-৬৭র অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল রামজীবনের সঙ্গে কথা বলার সময়। কিন্তু রামজীবন তো বলছিলেন ১৯৭৮ এর কথা। তখন তিনি ক্লাস নাইনে পড়েন। তার মানে এই ছ’য়ের দশকের মাঝামাঝি থেকে সাতের দশকের প্রায় শেষ পর্যন্ত ১০-১২ বছরে তো মানুষগুলোর স্রেফ বয়সই বেড়েছে। জীবনযাত্রার বদল হয়নি বিশেষ কিছুই। তাই বয়স যত বেড়েছে, দেখায় তার থেকে ঢের বেশি। ভাবছি আর মাথায় ঘুরছে শুধু একটা কথা, ৩০ কিলো কাঠের দাম এক টাকা।’ ‘সে বছর খুব বন্যা হল। আমাদের গ্রাম ছিল জঙ্গলের ধারে, নদী থেকে অনেকটা দূরে। নদীর ধারের গ্রামগুলো পুরো ডুবে গেছিল। আমাদের গ্রামেও জল ঢুকেছিল খুব। ভয়ঙ্কর দিন গেছে। রামজীবনের সঙ্গে কথা বলতে বলতে যে প্রসঙ্গটাতে আসতে চাইছিলাম সেখানে পৌঁছানোর আগেই এক ব্যাক্তি এসে হাজির হলেন তাঁর বাড়িতে। সাইকেলে চেপে। দেখে মনে হল, বয়স রামজীবনের থেকে অনেকটাই কম। পরনে সাধারণ জামা, প্যান্ট। পায়ে সস্তা চামড়ার চটি। মাথায় একটা গামছা শক্ত করে বাঁধা। রোদ থেকে বাঁচতে। সাইকেলটাকে গাছে হেলান দিয়ে দাঁড় করিয়ে রেখে খাটিয়ায় এসে বসলেন। গামছাটা খুলে মুখের ঘাম মুছলেন। আর সাইকেল থামানো থেকে বসা পর্যন্ত টানা তাকিয়ে থাকলেন অচেনা অতিথির দিকে। ‘আমার ভাই। মামার ছেলে।’ আগন্তুকের পরিচয় দিলেন রামজীবন মুর্মু। ‘আমার থেকে আট বছরের ছোট। আমরা মামা বাড়িতে থাকতে শুরু করার পরের বছর ও হয়েছিল।’ এবার পরিচয়টা পরিষ্কার হল। ভাল করে দেখলাম। রামজীবনের মতো চেহারায় ততটা বয়সের ছাপ পড়েনি। আর একটা তফাৎ আছে। রামজীবনের চোখে শহরের লোকের প্রতি যে বিস্ময়বোধ আছে, তা নেই তাঁর মধ্যে। রামজীবনের ভাইয়ের মুখ-চোখ থেকে স্পষ্ট, জটিল চরিত্রের শহুরে মানুষ ঢের বেশি দেখেছে সে। নাম জিজ্ঞেস করলাম।‘নকুল’আবার ফিরলাম রামজীবন মুর্মুর দিকে। এই এলাকায় রাজনৈতিক অবস্থা কেমন ছিল? পলিটিকাল গোলমাল, ঝামেলা…?‘আমি কোনও দিন রাজনীতি করিনি। নকুল করত। ঝাড়খন্ড পার্টি।’ঝাড়খন্ড পার্টি করতেন শুনে চমকে ঘাড় ঘোরালাম নকুল মাহাতোর দিকে। তারপর রামজীবনকে ফের জিজ্ঞেস করলাম, কিন্তু আপনি নিজে রাজনীতি করেননি কখনও? সমর্থন তো করতেন কাউকে। ‘বাবা-মামারা কংগ্রেসকে সমর্থন করত। আমরা দুই ভাইও ছোটবেলায় তাই করতাম। কংগ্রেসকে সমর্থন। তখনও গ্রামে সিপিআইএম আসেনি…’‘ছোটির কারবারটা বলো,’ খাটিয়ায় বসে ঘাম মুছতে মুছতে দাদার সঙ্গে এই আগন্তুকের কথাবার্তা শুনছিলেন চোখ ছোট করে, কপালে তিন-চারটে রেখা স্পষ্ট, রাজনীতির আলোচনা আসতেই রামজীবনকে থামালেন তাঁর ভাই। তারপর নকুল মাহাতো শুরু করলেন। ‘তখন আমি ছোট। এখানে একটা লোক ছিল ছোটি মাহাতো। কংগ্রেস করত। আমাদের থেকে অনেক বড়লোক। আমি, দাদা, গ্রামের আরও কিছু ছেলে ওর পেছনে পেছনে ঘুরতাম। আমাদের আশপাশের কয়েকটা গ্রাম মিলে ওই ছিল কংগ্রেসের নেতা। ’৭৮-৭৯ সাল থেকে সিপিআইএম আস্তে আস্তে আমাদের গ্রামে ঢুকতে শুরু করে। তার দু’এক বছরের মধ্যেই ছোটি কংগ্রেস ছেড়ে সিপিআইএমে চলে গেল। ওই হয়ে গেল পুরো এরিয়ার সিপিআইএম নেতা। এতে আমরা বেশিরভাগ ছেলে ওর ওপর খেপে গেলাম। ওর দলেই ছিল সহদেব মাহাতো, ছোটির ডানহাত। আমার থেকে কয়েক বছরের বড়। দাদার বয়সী। সহদেব, আমি, আরও কয়েকজন ঠিক করলাম, ছোটি মাহাতোর এই বেইমানি মানা যাবে না। তখনই আমরা ঠিক করলাম ঝাড়খন্ড পার্টি করব। ছোটি সিপিআইএমে চলে যাওয়ার পর সহদেবদা বলল, আর কংগ্রেস করে লাভ নাই। ছোটিকে শায়েস্তা করতে হলে ঝাড়খন্ড পার্টিই করতে হবে।’‘কেন কংগ্রেস করে লাভ নেই?’ থামিয়ে জিজ্ঞেস করলাম নকুল মাহাতোকে।‘কারণ, কংগ্রসের তখন দিন দিন অবস্থা খারাপ হচ্ছে। যদ্দিন সরকার ছিল ঠিক ছিল। ভোটে হারার পর কংগ্রসের অনেক ছোটখাট নেতাই সিপিআইএমে চলে গেল। কিন্তু ঝাড়খন্ড পার্টি তখন শক্তিশালী হতে শুরু করেছে আমাদের এলাকায়। নরেন হাঁসদার পেছনে তখন অনেক লোক। আমরা বুঝে গেলাম, সিপিআইএমের সঙ্গে লড়তে পারলে একমাত্র ঝাড়খন্ড পার্টিই পারবে। গ্রামের সব লোক নিয়ে মিটিং হল, ছোটিকে শায়েস্তা করা হবে কিনা জানতে। সবাই হ্যাঁ বলল, গ্রামে ঝাড়খন্ড পার্টির পতাকা তোলা হল।’ক্রমশ...।
জনতার খেরোর খাতা...
ঘাসফুলের দরজা - Rimel Sarker | ছোট বেলায় যখন বাবার কাছে চিঠি আসতো, সিদ্ধার্থের মনে হতো যেনো এক মেঘপিয়ন এক দিস্তা কাগজ জুড়ে লিখে পাঠিয়েছে “কেমন আছো, সিদ্ধার্থ?”। ওর এমন মনে হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক, ওকে কেউ কখনো জিজ্ঞেসই করে নি ও কেমন আছে কিংবা ও আছে তো? আসলে ওর উপস্থিতি কিংবা অনুপস্থিতি কখনোই কাউকে ভাবায় নি। জন্মের পর বাবা কে দেখেছে শুধু বড় বড় ফিল্ম বানাতে, টেলিভিশনে বুদ্ধিজীবিদের মতন বোধের বাণী শুনাতে, অথচ বাড়ি এলে কীভাবে সেই বোধের বাণী কর্পুরের মতন নিদারুণ ভাবে মিলিয়ে যায়, তাও দেখেছে ও। জন্মের পর ৬ বছর মাতৃস্নেহে লালিত, পালিত সিদ্ধার্থ খেলা শেষে ফিরে এসে দেখেছে রক্তাক্ত মায়ের মরদেহ। আজো ওর আবছা আবছা সেই স্মৃতি মনে পড়ে। বিকেলের পড়ন্ত রোদে, সহসা খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে দেখে, মায়ের দেহ নগ্ন, তখনো বুঝে উঠতে পারে নি যে, এক হায়েনা ছিড়ে খেয়েছে তার মাতৃদেহ। এটুকু বয়সে কী কোনো ছেলে বা মেয়ে বুঝবে এসব? সারা মেঝে তে রক্ত, মায়ের মাথা, বুক, যোনী থেকে রক্ত অনবরত পড়েই যাচ্ছে, কিছু বুঝে উঠতেই পারছে কী হলো, কীভাবে হলো। ছোট্ট ছেলে টা তার বাবা কে ডাকতে ডাকতে বেড়িয়ে গেলো ঘর থেকে, বাবা এলেন, দরজা আটকালেন আর বললেন ঈশ্বরের সাথে বাবার যুদ্ধতে বাবা হেরে গিয়েছেন, তাই হেরে যাওয়ার ফলস্বরূপ ঈশ্বর নাকি কেড়ে নিয়েছেন মা কে। বোকা সিদ্ধার্থ জানেও না ঈশ্বর ঘুমিয়ে আছেন, ঘুমকাতুরে ঈশ্বর কিছু জানেন না, তিনি জানেন না কিসের যুদ্ধ, জানেন না তিনি। সিদ্ধার্থের আজো মনে পড়ে, মায়ের ঘরের জানালা দিয়ে সোনালী সূর্য কেমন আলো দিচ্ছিলো , মনে হচ্ছিলো যেনো মায়ের মৃতদেহ থিয়েটারের স্পটলাইটের নিচে, আর রক্ত গুলো সূর্যের কান্না। জানালার দিকে তাকাতেই সিদ্ধার্থ একটা বাচ্চা মেয়ের অবয়ব দেখতে পেয়েছিল মিত্রদের বাড়িতে। মিত্রদের বাড়ির একটা ঘর আর ওর মায়ের ঘর একদম মুখোমুখি। সিদ্ধার্থ মেয়েটির পরিচয় জানার জন্য আকুল হয়ে বসেছিলো সেদিন, মনে প্রশ্ন জমে আছে;ও কি সব দেখেছে? কী হয়েছিলো আমার মায়ের সাথে? সিদ্ধার্থের বাবা বলেছিলো মা নাকি অনন্ত কালের রথে চড়ে বিদেয় নিয়েছেন, আর বলে গিয়েছেন ও ঘরে যেনো কেউ না ঢোকে। সিদ্ধার্থে বাবা লাশ সমেত সেই ঘর তালা বন্ধ করে দেন। আশ্চর্যের বিষয়, লাশ পঁচে গিয়ে তো দুর্গন্ধ বের হবার কথা, কিন্তু দুর্গন্ধ কখনোই বের হয় নি, বরং সিদ্ধার্থ পেয়েছে হাসনা হেনা এর সুবাস। কত শত চিঠি আসতো, আর সিদ্ধার্থ ভাবতো ওর মা চিঠি পাঠিয়েছে, কিংবা কেউ ওর কথা জিজ্ঞেস করে লিখেছে। মা এর মৃত্যুর পর সিদ্ধার্থ ভয়ানকভাবে একা, নিরপরাধ ঈশ্বরকে শত্রু ভেবে বড় হয়ে ওঠে। বাবা মানুষটা ওর খোঁজ না নিলেও সিদ্ধার্থ খুব ভালোবাসতো বাবাকে। আস্তে আস্তে এমন একাকিত্বকে বন্ধু করে বেড়ে ওঠা সিদ্ধার্থ চলে যায় কলকাতায় দর্শন নিয়ে পড়তে। ছোট বেলায় একবার সেনেকার “অন দ্যা শর্টনেস অফ লাইফ” পড়েছিলো, সেই থেকে দর্শন কে বড়ো ভালোবাসে। ম্যনিফেস্টোও পড়া হয়েছিলো তার। আসলে সিদ্ধার্থ বড়ো অদ্ভুত, একই সাথে মলয় ও শঙ্খকে ভালোবেসেছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বর্ষে পড়াকালীন ওর এক মেয়ের সাথে পরিচয় হয়। মেয়েটির নাম সিদ্ধা, কেমন যেনো মিল দুজনের নামে। পুরুষের স্বভাব, তার চোখ যদি একবার কোনো নারীকে নিস্পলকভাবে একাধারে দেখতেই থাকে, হৃদয় দূর্বল হয়ে যায় তার অজান্তেই। সিদ্ধার্থও এর ব্যতিক্রম নয়, সিদ্ধাকে ও প্রথম দেখে বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী তে, মেয়েটা ওর প্রিয় সেই ছোটবেলায় পড়া বইটিই খুঁজছিলো কিন্তু পাচ্ছিলো না। সিদ্ধার্থ মেয়েটির পাশে গিয়ে দাঁড়ালো আর জিজ্ঞেস করলো তুমি কি সেনেকার সেই বইটা খুঁজছো? কোন বইটা? সিদ্ধা পালটা প্রশ্ন করলো। অন দ্যা শর্টনেস অফ লাইফ? সিদ্ধার্থের এই প্রশ্নে অবাক হয়ে গেলো সিদ্ধা, আর মনে মনে ভাবতে লাগ্লো,সিদ্ধার্থ কীভাবে বুঝতে পারলো ও এই বইটিই খুঁজছে। সিদ্ধার্থ আবার বললো, আমি যেভাবেই বুঝতে পারি, এই নাও বইটি, এটা আমার মা আমায় দিয়েছিলো, আমার শেষ জন্মদিনে। সিদ্ধা বইটি নেয়, কিন্তু কোনো প্রশ্ন করে না, কারণ প্রশ্ন করেই বা কী লাভ? এই লাইব্রেরীতে দুই চাতক পাখির প্রশ্ন আর উত্তর পর্বে কী পৃথিবী কান দিচ্ছে? না দিচ্ছে না, সময় এমনিতেই তার পেটের মধ্যে আমাদের গ্রাস করে নিচ্ছে, তাই সময় কে নষ্ট করে কী লাভ? নষ্ট করার প্রতিশোধে সময় যদি আরো দ্রুত পেটের মধ্যে গ্রাস করে নেয়? যদি গলিয়ে ফেলে পেটে থাকা হাইড্রোকলিক এসিডে? তবে সব প্রশ্ন-উত্তর যদি সময় নষ্ট হতো পৃথিবীতে প্রেম বলে হয়তো কিছু হতো না। একটা মৃদু হাসি দিয়ে “ধন্যবাদ আপনাকে” বলে মৃদু মন্দ বাতাসের মতন বয়ে গেলো সিদ্ধা, সিদ্ধার্থের থেকে দূরে। তবে সিদ্ধার্থ বুঝেছিলো ও প্রেমে পড়েছে সিদ্ধার। নইলে মায়ের দেয়া প্রথম ও শেষ স্মৃতি, বইটি দিয়ে দিতে পারতো না। সিদ্ধাও কেমন, বইটি কবে ফিরিয়ে দেবে, বা সিদ্ধার্থের কবে প্রয়োজন একটি বার জিজ্ঞেসও করলো না। সিদ্ধার্থ তো বলল যে বইটা ওর শেষ জন্মদিনে পাওয়া। সিদ্ধা একবারও প্রয়োজন বোধ করল না সিদ্ধার্থকে জিজ্ঞেস করার, যে ওর জন্মদিন কবে ছিল? সিদ্ধার্থ ওর মা বেঁচে থাকাকালীন শেষ জন্মদিনকেই জীবনের শেষ জন্মদিন হিসেবে ধরে নেয়।ওর জন্ম ও মৃত্যুর খেলা, ওর মায়ের মৃত্যুর সাথে সাথেই শেষ। যে মাকে সিদ্ধার্থের এমন ভয়াবহ আত্মমৃতের মতন মনে পড়ে, সেই মায়ের দেওয়া শেষ স্মৃতিটুকু কী অবলীলায় বিলিয়ে দিলো সিদ্ধার কাছে! এই কি তবে প্রেম? না কি শুধুই মোহ? মোহ বোধ হয় নয়। মোহ হলে বই দিতো না, সেই তো ছোট বেলা থেকে বইকে বন্ধু হিসেবে ভেবে বড় হয়েছে। আর এই পৃথিবীতে চিরচিরায়ত ভাবে দেখা গিয়েছে প্রেমের ফলে বন্ধুও হারিয়ে যায়, প্রেমিকা হয়ে ওঠে সব থেকে বড় বন্ধু। সিন্ধু নদীকে বড় ভালোবাসে সিদ্ধার্থ, সিদ্ধাকে দেখার পরেই ওর মনে হয়েছিলো সিদ্ধা আর ও সিন্ধু নদীর পাড়ে বসে আছে, গান গাইছে; ওই মহাসিন্ধুর ওপার থেকে কী সঙ্গীত ভেসে আসে। সিদ্ধার্থ খুব ভালো গান গাইতো, সিদ্ধাও খুব ভালো গান গায় তবে রবি বাবুর গান একটু বেশিই ভালো লাগে ওর গলায়। এই ভ্রম থেকে সিদ্ধার্থ বেড়িয়ে আসে অপভ্রংশের মতন, ইতি টানে সমস্ত অমনিবাসের। সিদ্ধার সাথে ওর পরের দিন গঙ্গার পাড়ে দেখা হয়, মরা শুয়োরের পঁচা গন্ধ, কি এক বিভৎস পরিবেশ। সিদ্ধার্থ একটু বেশিই অবাক হয়ে যায় আর ভাবে সিদ্ধা এখানে কী করছে? এই মরা গঙ্গার ধারে ওর মতন মলিনা, শুভ্র,সুন্দর যৌবন রসে পরিপূর্ণ এক নারী তো এই পরিবেশের সাথে মানায় না। এই স্থান যে শুধুই বিপ্লবীদের, যে মরা গঙ্গায় ভেসে যায় লাশ, পঁচা গন্ধ সেখানে তো এই ঈশ্বরীর থাকা সাজে না। সিদ্ধার্থ সিদ্ধাকে গিয়ে বলে, কী মনে পড়ে আমায়? সিদ্ধা জবাবে বলে, “আপনার কথাই ভাবছিলাম”। সিদ্ধার্থ অবাক হয়ে বলে, “কী! তাই নাকি?!” সিদ্ধা বলে, “কেনো? কাল তো খুব মন পড়তে পারলেন আজ পারলেন না যে?” সিদ্ধার্থ কী উত্তর দেবে ভেবে না পেয়ে বলে “কাল একটু ঘোরে ছিলাম”। সিদ্ধা আর জিজ্ঞেস করে না কীসের ঘোর। বেচারা সিদ্ধার্থ ভাবে, “এ জীবনে যা কিছু চেয়েছি সেই কলহে ভীত ঘুমকাতুরে ঘুমন্ত ঈশ্বর তা কাড়িয়ে নিয়েছেন তার নামের বড়াত দিয়ে, সিদ্ধাকেও কি কেড়ে নেবেন তিনি?” ঠিক সেই মূহুর্তেই সিদ্ধা বলে , “চলুন, আজ আমি আর আপনি একসাথে মাতাল হবো, কলেজ স্ট্রীট এ একটা গোপন বার আছে শুনেছি, যাবেন নাকি?” । সিদ্ধার্থ এই আকস্মিক প্রস্তাবে একটু অবাক হয়, আর ভাবে “ভালো করে চেনা জানাই হলো না, আর একসাথে মাতাল হবো? আমি তো ওর প্রতি এমনিই মাতাল, ও কি সেটা জানে না?”। বোকা সিদ্ধার্থ জানেও না অবয়ব কী এবং তার স্মৃতিশক্তি সিদ্ধার থেকে কত দূর্বল, সিদ্ধা যে তাকে কাল প্রথম দেখাতেই চিনতে পেরেছিলো, তাই আর কোনো প্রশ্ন করে নি , সেটা সিদ্ধার্থ এখনো ধরতে পারে নি। বারে দুজনে উন্মাদের মতন মদ্যপান করে, সিদ্ধা হুশ এ থাকলেও সিদ্ধার্থের বাঁধ ভেঙে যায়। সিদ্ধার্থ কে সিদ্ধা ওর ফ্ল্যাটে পৌছে দিতে আসে। কিন্তু দুজনেই আজ মাতাল, হৃদয়ের ভেঙেছে বাঁধ, সিদ্ধার্থ সিদ্ধাকে টেনে নিয়ে চুমু তে লিপ্ত হয়ে পড়ে। দুজনে আজ দেহের সকল জরা জীর্ণতা কে সময়ের বালুর নিচে চাপা দিয়ে মিলিত হয়। সিদ্ধা আর সিদ্ধার্থ, দুজনেরই প্রথম বৈপরীত্য এর ছোয়া পাওয়া। পুরো রাত ভরে সিদ্ধার্থ চলে যেতে থাকলো সিদ্ধার তরমুজ আঙরাখার ভেতরে, মাথায় মলয়ের কবিতার লাইন : “সমস্ত নোঙর তুলে নেবার পর শেষ নোঙর০0 আমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে আর আমি পার্ছি না অজস্র কাচ ভেঙে যাচ্ছে কর্টেক্সে”শুভ্র সকালে, সিদ্ধার্থ অনুভব করে তার কপালের উপর ঝুলছে সিদ্ধার সাদা শুভ্র স্তন, স্তনে মাঝে একটা নীল রঙের লকেট। পৃথিবীর কোনো প্রেমই এমন কাব্যিক যৌনতা দিয়ে শুরু হয় কিনা সিদ্ধার্থ তা জানে না। তবে তার প্রেম এভাবেই শুরু হয়েছে, কালের বরপুত্র হবার ফসল হয়তোবা। ছোট বেলা থেকে ঘুণপোকার সিংহাসনে বসে, উৎপাদন পদ্ধতি নিয়ে চিন্তা করা ছেলেটা যখণ হাবিজাবি নিয়ে ভাবতে ভাবতে উন্মাদ হয়ে যায়, অন্তর টনিকেও কাজ হয় না, তখন সে যেতে চায় সাজানো বাগানের পরের স্টপেযে, আর সেই স্টপেজ হয়েই ধরা দেয় সিদ্ধা। একাকিত্ব কে সাথী করে বড় হয়ে ওঠা সিদ্ধার্থ এবার সিদ্ধাকে সাথী করে নেয়। সিদ্ধার্থ একা হলেও নিস্বঙ্গ ছিলো না, ওকে স্বঙ্গ দিতো বিড়ালের চোখ, লক্ষ্মী প্যাঁচার চাহনি, শিশিরের জলে ভেজা চালতা ফুলের সুবাস। তবে এবার সেই সাথে সঙ্গ দিচ্ছে হাসনা হেনা হয়ে আসা সিদ্ধা। মধুর প্রেম এভাবে গড়াতে থাকে, ঠিক বছর খানেকের মাথায় সিদ্ধার্থ সিদ্ধাকে কোনো একটি শোভাযাত্রায় দেখে এক অপরিচিত ছেলের হাত ধরে নাচতে, খুব অভিমান হয় সিদ্ধার্থের, ছোট বেলা থেকে কিছু না পেয়ে আসা মানুষটা যখন কাউকে আকড়ে ধরে বট গাছের শেকড়ের মতনই হয়তো আঁকড়ে ধরে। সেই আঁকড়ে ধরার ফল যে কী ভয়াবহ অভিমানের জন্ম দেয় সিদ্ধার্থ তা ভালো বুঝেছে এবার। সিদ্ধার ওপর অভিমান হয় নি ওর, আক্রোশ ও ক্ষোভ হয়েছে ঈশ্বরের প্রতি। এবার ক্ষীপ্ত হয়ে গিয়ে সিদ্ধার্থ এক চিঠি লেখে ঈশ্বরের কাছে,“ অন্তরীক্ষ ভেদ করে দেখি, দেখবার বদলে শুনতে পাই সহস্র ঘোর বিভিষীকা। যতদূর শুনি, শুনতে পাই প্রভুর যবনিকা। কেন? কেন এই বৈপরীত্য? আমি কি তোমার আঁতে খুব ঘা দিয়ে খুব বড় ভুল করে ফেলেছি? অমনিবাসের ইতি টেনে পাপের ক্যাফেতে বসে কালো গায়িকার ব্লুজ শুনতে তোমার কী খুব ভালো লাগে ঈশ্বর? তুমি কি কামাচ্ছন ওই কালো গায়িকার প্রতি? একটা অ্যালুমিনিয়ামের বাক্সে শব্দ কে জমা রাখবো, বাকশক্তিও কি জমা রাখা প্রয়োজন নয়? নইলে তোমার বিরুদ্ধে বার বার বলে উঠছি যে! সহস্র বৈদূর্যমণি ভেদ করে দূরে-দূরে এণ্ড্রোমেডো আর মিল্কিওয়ের চুম্বন দেখবে তুমি। আর সেই মৃত্যুজ্বালায় শত শত ঘাস্ফুল না ফড়িং হয়ে যায়! ব্যবিলিয়নের মতন আমি গুড়িয়ে দেবো তোমার প্রতি আমার নৈবেদ্যের থালা। তোমার যাকে দেখলে যৌনাকাঙ্খা বেড়ে যায়, সমুদ্রের বোন সেই কালোগায়িকা। কালো গায়িকার দেহের গন্ধে তুমি কেমন মোহাচ্ছন্ন, নইলে ওতো গুলো প্রাণ ঝড়ে গেলো তুমি কিছুই করতে পারলে না। ভুলেই গিয়েছিলাম তুমি তো ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দোষে ভুগছো। কেমন করে সেই এক জোড়া চোখ তাকিয়ে রইলো,অথচ তুমি ক্ষমাশীল হতে পারলে না ! ওহ তুমি তো শুধু জানো তোমার দোহাই দিয়ে কতগুলো প্রাণ কাড়িয়ে নিতে। বিশ্বাস করো মনে হচ্ছে ছুড়ি বেছানো কোনো বাগানে আমি উদ্ভ্রান্তের মতন শুয়ে আছি, শয্যাশায়ী। ঈশ্বর তুমি বড় নির্দয়, অবশ্য ঘুমিয়ে থাকা কোনো কিছুর হৃদয় কাজ করে না, নইলে যে পাখিকে ভালোবেসে ফেলে দিয়েছিলাম সকল জীর্ণতাকে আজ তারই উদ্দেশ্যে মহাশুন্যের দিকে তাকিয়ে বলতে হলো, ‘ পাখি, তোমায় ছাড়া কেমন করে কাটলো আমার বেলা, নিশীথ নিঝুম, কোথাও কেউ নেই, আমার মনে আপন কোণে হৃদয় বীণায় কী বিষাদ কণ্ঠস্বর বাজে, এর থেকেও বেদনা বিধুর নিদারুণ সুন্দর কিছু হতে পারে? বিট রুটের পাখি তুমি যে এত তাড়াতাড়ি ইউক্যালিপ্টাস এর চুড়োয় উঠে যাবে কেই বা জানতো? তোমার কথা যে আমি পিষে ফেলতাম না, পুষে রাখতাম…’ ঈশ্বর কি সুন্দর একটা অভিশাপ আমায় দিলে আবার, অবশ্য ঘুম থেকে জেগে ওঠে আর কীই বা করতে পারো তুমি! তোমার পোদে যদি একশো খানা লাথি মারতে পারতাম মনে বড় শান্তি পেতাম। তুমি ঘুম থেকে আর উঠো না, তুমি জেগে থাকলেই আরেক চাতক তার চাতক পাখিকে হারাবে, ঝড়ে যাবে কোনো বিপ্লবীর প্রাণ, পুঁজিবাদি পিতা তার সন্তান কে শেখাবে কীভাবে প্রেমের কারেন্সী চুমু থেকে মুদ্রাতে রুপান্তর করা যায়, কীভাবে নিজ চামড়ায় ত্বকের বিপরীতে মুদ্রাকে বসাতে হয়, তুমি শক্ত করে বন্ধ করো নিজেকে অ্যালুমিনিয়ামের বাক্সে।” এই চিঠি লেখার পর সিদ্ধার্থ সিদ্ধার থেকে অনেক দূরে চলে আসে। ১ মাস পর সিদ্ধা যায় সিদ্ধার্থের কাছে, ক্ষমা চায় তার এই ঠকবাজির জন্যে। ছোটবেলা থেকে একাকিত্ব কে আপন করে বেড়ে ওঠেছে সিদ্ধার্থ, কিন্তু সিদ্ধার অনুপস্থিতি ওকে যে ভয়াবহভাবে একলা করে দেবে ও সেটা বোঝে নি। না বুঝোক, ক্ষমাও করেনি। তবে সিদ্ধা যাওয়ার আগে কিছু সত্য উন্মচন করে যায়, আসলে সিদ্ধাই সেই অবয়ব যা সিদ্ধার্থ দেখেছিলো মাতৃ মৃত্যু কালে। সিদ্ধা আজ বলে গেল্ তার বাবা তার মাকে হিংস্র নেকড়ের মতন ধর্ষণ করে কামড়ে কামড়ে খেয়েছে,কিন্তু কেনো খাবে, নিজ স্ত্রীকে? আসলে ওর বাবা আদিম কালের নেকড়ে, নেকড়ের ছেলে হিসেবে ও জন্মেছে ফড়িং হয়ে, ওর মায়ের মতন। সিদ্ধার্থ চোখ বন্ধ করতেই সেই বিভিষিকাময় দৃশ্য ওর চোখের সামনে ভেসে আসে। সিদ্ধা কাঁদছে আর বলছে তোমায় খুব মনে পড়বে, আমায় একটি বার ক্ষমা করো না?! সিদ্ধার্থ জোসেফ স্ট্যালিন। তবে সিদ্ধার প্রস্থান কালে ও একটি কথা বলে, “কখনো যদি আমায় মনে পড়ে, ঘাস্ফুলের দরজায় ঠক ঠক করো, যদি সত্যি ভালোবাসো সাড়া দেবো”সিদ্ধা আর কথা বাড়ায় নি, ভাবতে ভাবতে চলে যায়, আর কথা বাড়িয়েই বা কী লাভ? পৃথিবী কি কান দিচ্ছে? সেই পুরোনো দিনের কথা মনে পড়তে থাকে সিদ্ধার। লাভ নেই, সময় প্রেম কে গ্রাস করে নিয়েছে। সিদ্ধার্থ এবার ফিরে যায় তার সেই বাড়িতে, বাবা কে দেখে এতো ঘৃণা হয় ওর, ঈশ্বরকেও এত ঘৃণা করে নি ও। ও ঠিক করে এবার মা আর ওর তরফ থেকে বাবাকে চিঠি পাঠাবে ডাকবাক্সে, সেই চিঠি বাবার কাছে পৌছেও যায়, আর সেই চিঠি পড়ে আত্মহত্যা করে ওর বাবা, চিঠিতে কী লেখা ছিলো তা সিদ্ধার্থ না জানিয়েছে কাউকে, না ওর বাবা। বাবার আত্মহত্যার পর, সিদ্ধার্থ ওর মায়ের ঘরের তালা ভাঙে, ভেতরে ঢুকে দেখে সেই রক্ত কে জল হিসেবে ব্যবহার করে মায়ের হাড়োর উপরে গজিয়ে উঠেছে ঘাস্ফুল, জানালার ধারে নীলকণ্ঠ, পায়ের কাছে হাসনা হেনা। সিদ্ধার্থ ঠিক করে নিজেকেও বন্দি করে ফেলবে ঘাস্ফুলের ঘরে, সিদ্ধার মনে বড় রকমের ঝড় বইছে, মনে হচ্ছে সিদ্ধার্থ ওর থেকে খুব খুব দূরে মহাকালের রথে চড়ে অন্তরীক্ষ ভেদ করে চলে যাচ্ছে, সিদ্ধা পাগলের মতন দৌড়ে ছুটে চলে যায় সিদ্ধার্থের বাড়ি, ততক্ষণে খুব দেরী হয়ে গিয়েছে। সিদ্ধার্থ নিজেকে বন্ধ করে নিয়েছে ওর মায়ের ঘরে। সিদ্ধা সারা বাড়ি তন্ন তন্ন করে খোঁজে, কিন্তু কোথাও সিদ্ধার্থ নেই, সবশেষে মায়ের ঘরের সামনে এসে দাঁড়ায়, দেখে তালা নেই দরজায়, ভেতর থেকে বন্ধ। সিদ্ধার্থের কথাটা ওর মনে পড়ে, “কখনো যদি আমায় মনে পড়ে, ঘাস্ফুলের দরজায় ঠক ঠক করো, যদি সত্যি ভালোবাসো সাড়া দেবো”সিদ্ধা দেখে ঘড়ের দরজা দিয়ে ঘাস্ফুল বের হয়ে আছে, ও ঠক ঠক করে কিন্তু কোনো সাড়া আসে না, সিদ্ধার্থকে আর দেখেনি পৃথিবী, কেঁদেছে অনেক।এতকিছুর পরও ওঁ পৃথিবীকে দেখছে সেই ঘর থেকে মায়ের কোলে শুয়ে।রাজভবনে শ্লীলতাহানি - সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায় | আজ থেকে বছর বারো আগে পার্ক স্ট্রিটে একটি ধর্ষণের অভিযোগ আসে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তদন্ত শেষ হবার আগেই বলেছিলেন 'সাজানো ঘটনা'। দলমত নির্বিশেষে বহু মানুষ সেই মন্তব্যের প্রতিবাদ করেন। তার মধ্যে এই অধমও ছিল। তারপর অবশ্য তদন্ত হয়, ধর্ষণ প্রমাণিত হয়, দোষীরা শাস্তি পায়।আজ থেকে ঘন্টা বারো আগে, রাজভবনে একটি শ্লীলতাহানির অভিযোগ আসে, রাজ্যপালের বিরুদ্ধে। বিজেপি নেতারাও অভিযোগ সরাসরি উড়িয়ে দেননি। শুভেন্দু অধিকারি বলেছেন "যদি সত্য হয়, তবে নিশ্চয়ই কেন্দ্রীয় সরকার পদক্ষেপ করবে"। ব্যতিক্রম বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। তিনি কেন্দ্রীয় সরকার এবং তার প্রতিনিধিদের হয়ে ব্যাট করার গুরুদায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়ে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় অভিযোগটাকেই "দুষ্কর্ম" আখ্যা দিয়েছেন। বলেছেন, (তৃণমূলের তরফ থেকে) পরিকল্পনা করেই এই অভিযোগ করা হয়েছে, রাজ্যপালকে বিপর্যস্ত করার জন্য। "আমার সন্দেহ" বা "হতেও পারে" এসব বললে তেমন বেঠিক কিছু হতনা, কিন্তু ন্যূনতম তদন্তের আগেই তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছেন। বস্তুত অভিযোগকারিণীকে চক্রান্তকারী বলেছেন। ফলে আজ থেকে বারো বছর আগে যে ভাবে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের প্রতিবাদ করেছিলাম, আজও সেইভাবেই বিকাশবাবুর মন্তব্যের বিরোধিতা করলাম। এক্ষেত্রে একটু বেশিই করা উচিত, কারণ, পার্কস্ট্রিট কান্ডের অভিযোগকারীরা কেউ সে অর্থে প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেননা। এখনকার অভিযুক্ত এতটাই প্রভাবশালী, যে পুলিশের অকুস্থলে যাওয়া অবধি নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন, কাগজে পড়লাম। এই মন্তব্যে নিয়ে ঝড় ওঠা উচিত। এক্ষেত্রে বিকাশবাবুর কথাই তাঁর দলের কথা কিনা জানিনা, না হলে তাঁরা এটা অনুমোদন করছেন কিনা, তাও জানিনা, তবে নজরে থাকবে।অবশ্যই আমি রাজ্যপালকে অভিযোগ শুনেই দোষী মনে করিনা। আমি মনে করিনা, কোনো অভিযোগ এলেই তা সত্য হয়ে যায়। পৃথিবীতে অনেক ব্যাপারেই রাজনৈতিক খেলাধুলো চলে, অনেক ক্ষেত্রেই চক্রান্ত-টক্রান্ত হয়। এই হাইভোল্টেজ পরিস্থিতিতে এই ব্যাপারেও চক্রান্ত একেবারেই অসম্ভব নয়। ফলে অভিযোগ শুনেই আদৌ রাজ্যপালকে দোষী ঠাউরাচ্ছিনা। একই সঙ্গে অভিযোগকারিণীকেও মিথ্যেবাদী ধরে নিচ্ছিনা। কী হয়েছে সেটা জানার জন্যই তদন্ত প্রয়োজন। রাজ্যপাল তদন্ত ব্যাপারটাই আটকে দিতে চান মনে হচ্ছে, এবং তিনি এতটাই ক্ষমতাশালী, যে সেটা পারেনও। তদন্তটাই যাতে আটকে না যায়, এবং যথাযথভাবে হয় দাবী সেইটুকুই। রাজ্যপালের বহু রাজনৈতিক অবস্থানের আমি বিরোধী, কিন্তু তার জন্য শ্লীলতাহানির অপরাধে প্রমাণের আগেই কাউকে আগেই দোষী বলে দেওয়া যায় বলে আমি মনে করিনা। অনেক নারীবাদী, অনেকবারই আমার এই অবস্থানের বিরোধিতা করেছেন। তাঁরা বলেন, প্রাথমিকভাবে অভিযোগকারিণীর কথাকেই সত্য ধরে নিতে হবে। এই ব্যাপারে তাঁরা কী অবস্থান নেন নজরে থাকবে। কিছু লেখার থাকলে ভবিষ্যতে দেখা যাবে।আর হ্যাঁ, তদন্তটা কীভাবে হবে? রাজ্যপালের তো সাংবিধানিক রক্ষাকবচ আছে। অনেক মিডিয়াতেই দেখলাম, বারবার এই ধরণের অভিযোগকে নজিরবিহীনও দাবী করা হচ্ছে। সেটা একেবারেই ঠিক না। আমার জীবদ্দশায় এর চেয়েও গুরুতর যৌন অপরাধের অভিযোগ দেখেছি রাজ্যপাল এনডি তিওয়ারির বিরুদ্ধে। সেক্ষেত্রে পুলিশ অভিযোগের তদন্ত করে, দোষী এই মর্মে রিপোর্ট দেয়। তিওয়ারিকে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। ফলে বিষয়টা নজিরবিহীন একদমই না। সাংবিধানিক কাঠামোতেই কীভাবে এগোতে হবে তার পরিষ্কার দৃষ্টান্ত আছে। মোদী জমানায় তো ভারতীয় গণতন্ত্র পুনরাবিষ্কৃত হলনা, এসবের নজির আছে। খুব বেশিদিন আগের ঘটনাও না, সাংবাদিকরা পেশার ব্যাপারে একটু সিরিয়াস হলে মনে করতে বা খুঁজে বার করতে পারবেন।অক্কা পাওয়ার উৎস অনুসন্ধান - Argha Bagchi | অক্কা পাওয়া বাক্যবন্ধের সরল অর্থ মারা যাওয়া। সংসদ, ঢাকা বাংলা একাডেমি, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ও হরিচরণ থেকে অক্কা ও অক্কা পাওয়া পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, অভিধানকারেরা অক্কা শব্দের অর্থ বিশ্লেষণ করেই অক্কা পাওয়া বাগধারার উৎস খোঁজার চেষ্টা করেছেন। ফার্সি আকা মানে প্রভু, মালিক বা ঈশ্বর। সুতরাং ঈশ্বরপ্রাপ্তি অনুষঙ্গে মারা যাওয়া অর্থে অক্কা পাওয়া বাক্যবন্ধের জন্ম। আবার, তামিলে আক্কা মানে ভগিনী বা মাতা। লাতিন acca. মানেও মাতা। ফলে হরিচরণ বলছেন, বৈষ্ণবদের কেষ্টপ্রাপ্তির মত শাক্তদের অক্কা পাওয়া, মানে মাতারূপে ঈশ্বরকে প্রাপ্তি। উপরোক্ত ধারণাগুলি পড়লে মনে হয়, সমীকরণ মেলানোর জন্য যথেষ্ট কষ্টকল্পনার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। বরং, অক্কা পাওয়ার অক্কা শব্দটাকে একক অক্কা শব্দ থেকে পৃথক করে ভাবলে সহজ সমাধান সম্ভব। বাংলা ভাষার ব্যবহারে জীবনরক্ষা বা প্রাণরক্ষা শব্দদুটিও মৃত্যুলাভ অর্থে পাওয়া যায়। প্রাকৃত উচ্চারণে রক্ষা থেকে অক্কা হওয়া সম্ভব। সেক্ষেত্রে প্রাণ রক্ষা পেল বা জীবন রক্ষা পেল সহজেই অক্কা পেল-তে রূপান্তরিত হতে পারে। কিন্তু রক্ষা পাওয়া মানে তো রেহাই পাওয়া। তাহলে জীবন থেকে রেহাই পাওয়া অর্থে মৃত্যুকে দেখার দর্শন কি আমাদের সমাজে প্রচলিত ছিল! সম্ভবত এর মূলে রয়েছে জৈন দর্শনের প্রভাব। পূর্ব ভারতে জৈন ধর্মের যথেষ্ট প্রসার ছিল। জৈন মতে জন্ম দুঃখজনক হলেও মৃত্যু মানে আনন্দ, মৃত্যু মানে মুক্তি। ফলে জীবন থেকে রক্ষা পাওয়া আর অক্কা পাওয়া একই কথা, কেবল অপরিমার্জিত উচ্চারণের কারণে রক্ষা হয়ে গেছে অক্কা। এর সাথে ফার্সি আকা বা তামিল আক্কার গোজামিল খোঁজা নিষ্প্রয়োজন। আপনাদের কী মনে হয়? এ বিষয়ে আরো অনুসন্ধান হওয়া কি বাঞ্ছনীয় নয়?
ভাট...
 &/ | গরু ছাগল বাঘ কুকুর বেড়াল ---যেকোনো প্রাণীই আঁকা কঠিন ,বেশ কঠিন .
&/ | গরু ছাগল বাঘ কুকুর বেড়াল ---যেকোনো প্রাণীই আঁকা কঠিন ,বেশ কঠিন . &/ | একটা থ্যাবড়া গোল আভাঁগার্দ ছবি আপলোড করতে গেলাম, গেল না।
&/ | একটা থ্যাবড়া গোল আভাঁগার্দ ছবি আপলোড করতে গেলাম, গেল না।  দ | কিন্তু এখনো ছবি আপলোডের ব্যপারটা ফিক্স হল না। কি মুশকিল!
দ | কিন্তু এখনো ছবি আপলোডের ব্যপারটা ফিক্স হল না। কি মুশকিল!
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাদয়াময়ী-সন্ধেবেলা - জগন্নাথদেব মণ্ডল
০৩ মে ২০২৪ | ৮১ বার পঠিতসন্ধেবেলা দয়াময়ীর এই কথাটুকু মনে পড়ল দয়াময়ীর দয়াময়ী ছাড়া কেউ নেই। আজানে তখন আকাশ ফেটে গেছে, গলে গলে নামছে অন্ধকারের প্রথম দিককার রঙ। পেয়ারা ফুলের মতো মুখ নিয়ে ও কান পেতে শুনল সরসর করে কোথাও কিছু একটা বাজছে। বোঝা গেল, একেবারে একা একটা তালগাছ মাঠের মাঝখানে হাওয়ায় পাতাদের কাঁপাচ্ছে। ভাত খেতে বসে ওঁর বুক উদাস হয়, একজন কেউ থাকলে ভালো হত। এই এতবড়ো নীলসাদা রঙীন বাড়ি,দেওয়ালে সদ্য চুনকামের গন্ধ বুকে উঠে আসে। চিরকাল মাটির ঘরে, পাতার ঘরে দিন কেটেছে। সরকারি প্রকল্পের একা একা বিধবার মতো ফাঁকা বাড়িতে অস্বস্তি হয়, সন্ধ্যামালতী ফুলের চেয়েও নরম মা দেখে যেতে পারল না এই ঘরদোর। নিজেকে নিজের জল গড়িয়ে নিতে হলে, ভাতের পাতে কাঁচালঙ্কা-নুন বারবার আনতে যেতে হলে ভালো লাগে না। এতো যত্নে করা রান্নাবান্না অর্থহীন হয়ে পড়ে যতোক্ষণ না কেউ সেই খাবার খেয়ে একমুখ হাসিতে তারিফ করে ওঠে। চিংড়ি মাছের মাথার চচ্চড়ি তারিফ না করলেও মুখ তুলে অন্তত বলুক বিচ্ছিরি হয়েছে খেতে, এ রান্না খাওয়া যায় না। পরের দিন সে সব মায়ামমতা ঢেলে এমন মোচাঘন্ট রাঁধবে সেদ্ধ ছোলার তুক কাজে লাগিয়ে যে, কর্তাকে থালা অবধি চেটে খেতে হবে।
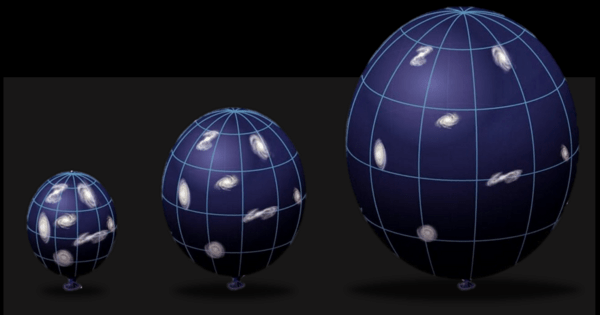 হরিদাস পাল
হরিদাস পালমহাবিশ্বের রহস্য - অনির্বাণ কুণ্ডু
০৩ মে ২০২৪ | ২৭ বার পঠিত১৯৩৩ সালে ফ্রিৎজ জুইকি নামে এক বিজ্ঞানী দেখালেন, মোট পরমাণুর হিসেব থেকে ছায়াপথের ভর বের করতে গেলে একটা গোলমাল হচ্ছে। ছায়াপথের স্পাইরাল বাহুতে যে সমস্ত নক্ষত্র আছে, তারা সকলেই ছায়াপথের কেন্দ্রের চারদিকে আস্তে আস্তে ঘুরছে। ছায়াপথের দৃশ্যমান ভরের প্রায় পুরোটাই এই কেন্দ্র অঞ্চলে অবস্থিত (কেন্দ্রের গল্পটা সংক্ষেপে বলেছি শেষের দিকে। সেখানে যে ঠিক কী আছে, তা দেখানোর জন্যে এই বছর, ২০২০ সালে, রাইনহার্ট গেঞ্জেল এবং আন্দ্রেয়া গেজ নামে দুই বিজ্ঞানী নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন)। কিন্তু তাহলে ওই নক্ষত্রদের ঘোরার বেগ যত হওয়া উচিত, পাওয়া যাচ্ছে তার চেয়ে অনেক বেশি। জুইকি বললেন, এর একমাত্র ব্যাখ্যা মহাবিশ্বের সব ভরই দৃশ্যমান নয়। অনেকটা জিনিস আছে যা আমরা চোখে (অর্থাৎ যন্ত্রপাতি দিয়ে) দেখতে পাই না, শুধু তার মহাকর্ষীয় টান অনুভব করতে পারি। এর নাম দিলেন ডার্ক ম্যাটার বা কৃষ্ণবস্তু।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালমারিয়াজ ক্রিয়েশন ও গুরুচন্ডা৯ - শুরু হোক পথ চলা - Maria’s Creation
০৩ মে ২০২৪ | ৭৩ বার পঠিততো সেই ভাবনা থেকেই গাঁটছড়া হল গুরুচণ্ডা৯র সাথেও – যে গুরুচণ্ডা৯ আমার আরেক ভালোলাগার জায়গা, যেখানে এসে আমি প্রাণভরে নিশ্বাস নিই। এ বছর বইমেলায় গুরুচণ্ডা৯র স্টলে ছিল মারিয়াজ ক্রিয়েশনের বেশ কিছু সৃষ্টি, স্টলসজ্জা এবং বিক্রি, দুইএর জন্যই। এই যৌথ উদ্যোগের পরবর্তী ধাপ হিসাবে তাই গুরুর পাতায় তুলে আনলাম আমার কিছু সৃষ্টি ।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালকিষেণজি মৃত্যু রহস্য - পর্ব ৭ - বিতনু চট্টোপাধ্যায়
০৩ মে ২০২৪ | ৪২ বার পঠিত‘কারণ, কংগ্রসের তখন দিন দিন অবস্থা খারাপ হচ্ছে। যদ্দিন সরকার ছিল ঠিক ছিল। ভোটে হারার পর কংগ্রসের অনেক ছোটখাট নেতাই সিপিআইএমে চলে গেল। কিন্তু ঝাড়খন্ড পার্টি তখন শক্তিশালী হতে শুরু করেছে আমাদের এলাকায়। নরেন হাঁসদার পেছনে তখন অনেক লোক। আমরা বুঝে গেলাম, সিপিআইএমের সঙ্গে লড়তে পারলে একমাত্র ঝাড়খন্ড পার্টিই পারবে। গ্রামের সব লোক নিয়ে মিটিং হল, ছোটিকে শায়েস্তা করা হবে কিনা জানতে। সবাই হ্যাঁ বলল, গ্রামে ঝাড়খন্ড পার্টির পতাকা তোলা হল।’
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালদোলজ্যোৎস্নায় শুশুনিয়ায় - ৭ - সমরেশ মুখার্জী
০৩ মে ২০২৪ | ২৬ বার পঠিতআশির দশকে যাদবপুরের কয়েকটি ছাত্রছাত্রী শুশুনিয়া পাহাড়ে গেছে শৈলারোহণ অভ্যাস করতে - সেই ভিত্তিতে এই আখ্যান … নানা বিক্ষিপ্ত চিন্তা এভাবেই সুসংহত ভাবনায় রূপান্তরিত হয়। না হলে চর্চার অভাবে ফিকে হয়ে যায়। অধিকাংশ মানুষ অকারণে অপমানিত হওয়ার ঘটনা সহজে ভুলতে পারে না, মনের মধ্যে জমা থাকে ঋণাত্মক অভিজ্ঞতার স্মৃতি। ক্ষেত্রবিশেষে তা উপরিতলে ভেসে ওঠে। তবে তা উপেক্ষা করতে পারা সেই ঋণাত্মক মানবিক প্রবণতার ওপর শুভবুদ্ধির জয়। এটা ধণাত্মক উত্তরণ। এ জিনিস আয়ত্ত করা সহজসাধ্য নয়। গভীর উপলব্ধি ও আত্মসংযমের ব্যাপার। তবে কখনো উপেক্ষা বা ক্ষমার আপাত মোড়কের অন্তরালে থাকতে পারে অক্ষমতা, কাপুরুষতা..
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালসস্তার রাজনীতি চাষের মাশুল - Bhattacharjyo Debjit
০৩ মে ২০২৪ | ১২৩ বার পঠিতদেশের শ্রমজীবী মানুষের রাজনৈতিক চেতনা বিকাশ ঘটানোর বদলে পরনির্ভরশীল করে তোলার এমন সস্তার রাজনীতির চাষ, শ্রমজীবী মানুষের উন্নত-জীবনের ভাবনাকে আটকে দেওয়ার কাজ যে কতটা ক্ষতিকর তা এখন হারে হারে টের পাওয়া যায়। এর ফলে রাষ্ট্র শ্রমিকের কাজের বোঝা বিনা বিরোধিতায় ক্রমাগত বাড়িয়ে চলে, শ্রমজীবী মানুষকে ধর্মীয় মোহে মাতিয়ে তুলে একের পর এক জনবিরোধী আইনগুলিকে জ্যান্ত করে লগ্নি পুঁজির স্বার্থ রক্ষা করে, একের পর এক স্ব-তান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিজেদের কব্জায় নিতে পারে।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালবৈঠকি আড্ডায় ১৫ - হীরেন সিংহরায়
০২ মে ২০২৪ | ১৮ বার পঠিতএই চূড়ান্ত ব্যক্তি স্বাধীনতার দেশে কে কোন পোশাক পরবে , বিশেষ করে মহিলারা, তা মিটিং ডেকে ঘোষণা করতে পারি না, বোর্ডে লিখে দেওয়া অকল্পনীয় । তুল কালাম ঘটতে কতক্ষণ । দৈনিক সান পত্রিকায় বেনামে লেখা হবে , “ লন্ডনের ব্যাঙ্কে স্বৈর শাসন , ভারতীয় মূলের অফিসার দ্বারা নারী মর্যাদার অপমান “। আমার চাকরি নিয়ে টানাটানি । অতএব অত্যন্ত ট্যাকটফুলি আমার তৎকালীন সেক্রেটারি , বারমিংহামের মারিয়া লালিকে কে বললাম, তুমি এটা একটু হাওয়ায় ভাসিয়ে দাও দিকি। আমি বলেছি কেউ যেন জিনস অথবা ট্রেনার জুতো পরে না আসে । মেয়েদের পোশাক সংযত , আর ছেলেদের ক্ষেত্রে টাই বাদে সুট পরলেই সেটা ইনফরমাল হয়ে গেলো অথবা কম্বিনেশান – রঙ মিলিয়ে জ্যাকেট ও ট্রাউজার। টি শার্ট আউট অফ কোয়েসচেন , পুরো হাতা শার্ট কিন্তু টেকনিকলার জামা বাদ । কালো বাদামি যাই হোক না কেন, পরতে হবে বন্ধ জুতো ।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালভ্রমণ কাহানি(৬) :উপল মুখোপাধ্যায় - upal mukhopadhyay
০২ মে ২০২৪ | ৬৯ বার পঠিত হরিদাস পাল
হরিদাস পালকাইজার গান্ধী - Nabhajit
০২ মে ২০২৪ | ৪৬ বার পঠিত হরিদাস পাল
হরিদাস পালরিলায়েন্সের পুঁজিই আমাদের পুঁজি - সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায়
০১ মে ২০২৪ | ৩৩০ বার পঠিতবাংলায় কেন এরকম হয়না, এটা নেটে সাড়ে তিন মিনিট সার্চ করলেই জানা যেত। জানা যেত, যে, সিনেমাটার অন্যতম প্রযোজক শ্রীমতি জ্যোতি দেশপান্ডে ( সার্চ করেই জানলাম), যিনি ভায়াকম ১৮র সিইও, যেটা মূলত রিলায়েন্সের কোম্পানি । নারী থেকে ফুটবল, সিনেমা থেকে রাজনীতি, সবকিছুই এখন যাঁদের হোলসেল বিজনেস, যাঁদের অনুমতি ছাড়া একটা পাতাও পড়েনা নানা বাগানে, এই সিনেমার পিছনে সেই আম্বানিদের কল্যাণ এবং দক্ষিণহস্ত আছে, তাই এইরকম 'ব্যতিক্রমী' সিনেমা হয়েছে হিন্দিতে। আম্বানি বা অন্য বড়ো খেলোয়াড়রা ( যেমন নেটফ্লিক্স বা অ্যামাজন) কখনই বাংলা সিনেমায় বিনিয়োগ করবেননা, তাই বাংলায় হবেনা। আশ্চর্যের কিছুই নেই, এটাই যুগের হাওয়া। বিশেষ করে আম্বানিদের নিয়ে এ কোনো নতুন কথা নয়, যে তাঁরা ওয়েস্ট-ইন্ডিয়া-কোম্পানির অংশ, পূব দিকে থেকে সম্পদ জমা করেন পশ্চিমে, মুকেশ এই সেদিন নিজেই বলেছেন, তাঁরা আদ্যন্ত গুজরাতি, বেশিরভাগ বিনিয়োগই ওইদিকে। ফলে বাংলায় কেন হয়না, কেন হিন্দিতে হয়, প্রশ্নটা "ওদিকে বিয়ে খেতে বিল গেটস আসে, এদিকে কেন আসেনা"র মতোই বেকার এবং অশ্লীল।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালমুক্ত বন্দীশালায় কিছুক্ষণ - ৩ (শেষ) - সমরেশ মুখার্জী
০১ মে ২০২৪ | ১৩০ বার পঠিত"একা বেড়ানোর আনন্দে" - এই সিরিজে আসবে ভারতের কিছু জায়গায় একাকী ভ্রমণের অভিজ্ঞতা। এটি পর্ব - ২৫ - করণ বলে, বাবুজী, আপনি তো আমায় সিনেমায় এ্যাক্টিং করার মতো করতে বলছেন। আমি কী পারবো? বলি, চেষ্টা করে দ্যাখোই না। তবে চাপ নিয়ো না, এসব আমার নিছক খেয়াল। ওদের নিস্তরঙ্গ জীবনে বেড়াতে আসা এক প্রবীণ বাঙ্গালী আঙ্কলের খেয়াল দেখে করণও মজা পায়। স্পোর্টিংলি বলে, চলুন তাহলে দেখি, আপনি যা বলছেন, পারি কিনা
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাভক্স পপুলি - যদুবাবু
৩০ এপ্রিল ২০২৪ | ৭৮০ বার পঠিতধরা যাক আমাদের n-সংখ্যক ভোটার আছে, n বিজোড় সংখ্যা (অর্থাৎ “টাই” অসম্ভব)। প্রত্যেক ভোটারের ঠিক বিকল্পে ভোট দেওয়ার সম্ভাবনা ধরা যাক pc, এবং সবার ভোট পড়ে গেলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে “মেজরিটি রুল” অনুযায়ী, অর্থাৎ যে সবথেকে বেশি ভোট পাবেন, সেটিই আমাদের গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত। কনডরসে-র উপপাদ্যে এও ধরে নেওয়া হয়, যে, প্রত্যেক ভোটার ‘স্বতন্ত্র’, ‘দক্ষ’ এবং ‘আন্তরিক’। ‘স্বতন্ত্র’ – অর্থাৎ যে যার নিজের ভোট দিচ্ছেন বা একজনের পছন্দ আরেকজনকে প্রভাবিত করে না। ‘দক্ষ’ – অর্থাৎ, প্রত্যেকের ঠিক বিকল্প খুঁজে নেওয়ার সম্ভাবনা অর্ধেকের থেকে বেশি, যত সামান্যই হোক, এক্কেবারে র্যান্ডম গ্যেস অর্থাৎ ইকির-মিকির-চামচিকির করে আন্দাজে যা-ইচ্ছে-তাই একটা বোতাম টিপে দেওয়ার থেকে তার প্রজ্ঞা বা দক্ষতা একচুল হলেও বেশি। আর শেষ অ্যাজ়াম্পশনের কথা আগেও লিখেছি, ভোটার-রা ‘আন্তরিক’, সিরিয়াস-ও বলা যায়—কেউ ইচ্ছে করে ভুলভাল ভোট দিয়ে নষ্ট করছেন না।
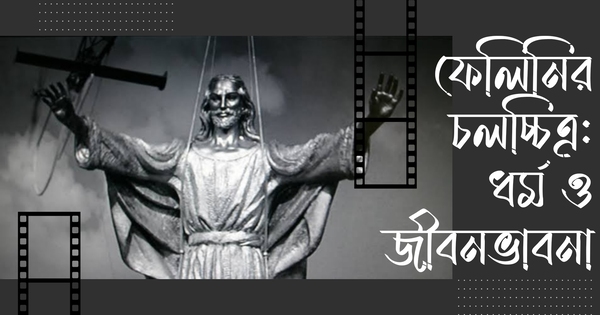 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাফেদেরিকো ফেলিনির চলচ্চিত্র – ধর্ম ও জীবন ভাবনা - শুভদীপ ঘোষ
২৯ এপ্রিল ২০২৪ | ৯০৭ বার পঠিতস্টেট ও চার্চকে সম্পূর্ণ পৃথক করে দিতে হবে। রাজ্য পরিচালনার কাজে চার্চ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না এবং রাজ্যও চার্চের কাজে হস্তক্ষেপ করবে না। রাজ্য পরিচালনার কাজে রোমান ক্যাথলিক চার্চ সরাসরি হস্তক্ষেপ করত। নিয়ম-শৃঙ্খলা বলবৎ ছিল, যাকে বলা হত খৃষ্টীয় অনুশাসন। কিন্তু পরবর্তীতে স্টেট ও চার্চের এই বিযুক্তিকরণই ছিল সেকুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতার আদি সংজ্ঞা। নিয়ম-শৃঙ্খলা অর্থাৎ অনুশাসনের ভাবনা নিশ্চয়ই আদিম যুগে ছিল না, গুহামানবের যুগে ছিল না। জৈবিক বিবর্তনের পথ ধরে সমাজ তৈরি হয় এবং সেই পথেই কোনো একসময় নিশ্চয়ই নিয়ম- শৃঙ্খলা বা অনুশাসনের ভাবনা এসেছিল। ধর্মের উৎপত্তি ও সামাজিক অনুশাসন কি যমজ সন্তান! প্রাচ্যের প্রাচীন ধর্মগুলিই হোক বা আব্রাহামিক (সেমেটিক) ধর্মগুলিই হোক, পাপ-পুণ্যের ভয় দেখানো ব্যাপারটা ধর্মীয় অনুশাসন কায়েম রাখার পিছনে কাজ করত, তা হয়ত অস্বীকার করা যাবে না।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালমুক্ত বন্দীশালায় কিছুক্ষণ - ২ - সমরেশ মুখার্জী
২৯ এপ্রিল ২০২৪ | ১৬২ বার পঠিত"একা বেড়ানোর আনন্দে" - এই সিরিজে আসবে ভারতের কিছু জায়গায় একাকী ভ্রমণের অভিজ্ঞতা। এটি পর্ব - ২৪ - অনেকের ধারণা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড মানে ১৪ বা ২০ বছর। তা কিন্তু নয়, সরকার চাইলে কাউকে আমৃত্যু কারাগারে বন্দী রাখতে পারে। তবে নতুন, হার্ডকোর অপরাধীদের জন্য কারাগারে স্থান সংকুলানের জন্য জেলারের সুপারিশে সাত দশ বছর জেল খাটা কিছু শান্ত, ভদ্র, নিরীহ দণ্ডিতদের মুক্ত বন্দীশালায় এনে রাখা হয়। তাতে বন্দী পিছু সরকারের খরচও হয় অনেক কম
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাবিপ্লবের আগুন - পর্ব তিন - কিশোর ঘোষাল
২৯ এপ্রিল ২০২৪ | ৩৩৬ বার পঠিতএখন এই বেলা আড়াই প্রহরে রাজপথে পথচারীর সংখ্যা বেশ কম। কয়েকজন রাজপুরুষ ঘোড়ার পিঠে দুলকি চালে নগর পরিদর্শন করছে। সকালের প্রথম প্রহরান্ত থেকেই বিপণিতে ক্রেতাদের ভিড় জমতে থাকে। এখন পথের দুধারের বিপণিগুলিও প্রায় ক্রেতাহীন। সূর্যের তেজ যত বাড়তে থাকে নাগরিক ক্রেতারা গৃহাভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে। এই সময় বরং আশপাশের গ্রাম থেকে আসে গ্রাম্য লোকজন - ঘোড়া কিংবা গোশকটে। তাদের আশাতেই বণিকরা শূণ্য বিপণিতে ধৈর্য ধরে বসে থাকে। পড়শি বণিকদের সঙ্গে গল্পসল্প করে সময় কাটায়। সাধারণতঃ এই গ্রাম্য ক্রেতারা সরল হয়। কথার তুবড়িতে তাদের ভুলিয়ে ফেলা যায় সহজেই। তাদের সঙ্গে কিছুটা তঞ্চকতা করে, নাগরিক ক্রেতাদের তুলনায় বেশ দুকড়ি উপরিলাভ করে নিতে পারে বণিকেরা। তবে আজকাল গ্রাম্য ক্রেতারাও শহরমুখো হচ্ছে কম। আজকাল কিছুকিছু বণিক, গাধার পিঠে, বলদের গাড়িতে পসরা সাজিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ায়। ঘরের মেয়েরা সরাসরি তাদের পছন্দ মতো বাসন-কোসন, রান্নার সরঞ্জাম, মশলাপাতি, কাপড়চোপড়, প্রসাধনী সামগ্রী হাতে নিয়ে, নেড়েচেড়ে, দেখেশুনে কিনতে পারে। কারণ শহরে আসে পুরুষরা।
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাভুলভুলাইয়ায় ছনেন্দ্রনাথ - রমিত চট্টোপাধ্যায়
২৭ এপ্রিল ২০২৪ | ৪৮১ বার পঠিতসেদিন সকালে তেতলার পিসিমার ঘরে বসে এক মনে ড্রয়ার ঘাঁটছিল ছেনু। ওটা আসলে মহারাজ ছনেন্দ্রনাথের রত্ন ভান্ডার। যত রাজ্যের উদ্ভট জিনিসের ভিড় থেকে মনমতো জিনিসগুলো নেড়েচেড়ে দেখতে দেখতে একটা বল্টু লাগানো লম্বা স্ক্রু ভারি পছন্দ হয়েছে, বল্টুটা খুলতে যাবে, ঠিক এমন সময় দোতলা থেকে হইচই কানে এল। শেয়ালদার মতো ব্যস্ত এলাকায় হট্টগোল তো সর্বক্ষণ লেগেই আছে, কিন্তু এই হইচই এর শব্দটা ভারি মিঠে, আর তার মধ্যে একটা চেনা চেনা গলাও উঁকি দিচ্ছে, তাই ছেনু আর থাকতে পারলো না, স্ক্রুটা ফেলে রেখে সিঁড়ি দিয়ে এক দৌড়ে নিচে নেমে এল।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালমুক্ত বন্দীশালায় কিছুক্ষণ - সমরেশ মুখার্জী
২৭ এপ্রিল ২০২৪ | ২৭২ বার পঠিত"একা বেড়ানোর আনন্দে" - এই সিরিজে আসবে ভারতের কিছু জায়গায় একাকী ভ্রমণের অভিজ্ঞতা। এটি পর্ব - ২৩ - এই লেখায় চরিত্রগুলির নাম উল্লেখ না করতে আমি রঘুবীর মীনাজীর কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই জায়গাটিরও আসল নামের বদলে করলুম - সূরজনগর - After all what's in a name?
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাস্লোভাকিয়া ২ - হীরেন সিংহরায়
২৭ এপ্রিল ২০২৪ | ৩১৫ বার পঠিতএকদা ইউরোপের মাঝখানে কোথাও বসবাস করতেন স্লাভ জাতি। কালে খাদ্যের অকুলান হলো, নিয়মিত তুরকিক অভিযানে জীবন বিপর্যস্ত–দেড় হাজার বছর আগে ভাগ্য সন্ধানে তাঁরা ইউরোপের তিন দিকে বেরিয়ে পড়লেন। পোল্যান্ডের প্রচলিত লোকগাথা অনুযায়ী তিন স্লাভিক ভাই, লেখ চেখ রুশ গেলেন তিন দিকে–উত্তর দিকে লেখ, পুবে রুশ দক্ষিণে চেখ। লেখ বাসা বাঁধলেন আজকের পোল্যান্ডে (লেখ নামক বিয়ার তাঁর নামকে অমর করে রেখেছে) বেলারুশ; রুশ যেখানে থামলেন সেটি আজকের রাশিয়া, ইউক্রেন (আক্ষরিক অর্থে সীমানা), চেখ ভাই গেলেন দক্ষিণে, আজকের বলকান অবধি। কালক্রমে খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করলেন সকলে। পশ্চিমে কেন যান নি তার কোন ব্যাখ্যা পাই নি। হয়তো বর্বর গথ ভিসিগথ জাতির নৃশংস আচরণের কাহিনী শুনেছিলেন অথবা এই তিন অঞ্চলে তাঁরা পেলেন বাসযোগ্য ভূমি; লোভ বাড়ান নি।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালফারাও-এর দেশে কয়েকদিন - অন্তিম পর্ব - সুদীপ্ত
২৭ এপ্রিল ২০২৪ | ১৭৬ বার পঠিতএরপর আমরা চললাম আরেকটি গন্তব্যে, মাঝসমুদ্রে ব্যানানা বোটে চড়তে। এই বোট বা নৌকোটি রাবারের তৈরী আর হাওয়া ভরে ফোলানো। দেখতে ঠিক পাকা কলার মতো-ই আর রং-ও হলুদ। উপরে ছয় জন করে বসতে পারে, একটি করে আঙটা লাগানো আছে ধরে থাকার জন্যে। এর সামনে একটি মোটরচালিত বোটে এই ব্যানানা বোট বেঁধে দেওয়া হয় আর দুরন্ত গতিতে মোটরবোট চলতে শুরু করলে এই ব্যানানা বোট-ও কোনোমতে টাল সামলে পাল্লা দিয়ে জল কেটে দৌড়োয়। জলের ফোয়ারা, দুরন্ত গতির সাথে শরীরের ভারসাম্য রাখা আর অসীম সমুদ্রের বুকে ছুটে চলা, একেবারে রোমহর্ষক ব্যাপার বটে। সবাই মিলে খুব উপভোগ করলাম এই রাইড।
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাক্যালিডোস্কোপে দেখি - বৃষ্টি - অমিতাভ চক্রবর্ত্তী
২৭ এপ্রিল ২০২৪ | ২৫৯ বার পঠিতপ্রকৃতি একটু একটু করে খুলে দিচ্ছিল তার জাদু-দরজা। ঘরের একদিকের দেয়ালের পাশে ছিল লম্বা লম্বা পাতার কিছু গাছ। তাতে অদ্ভুত দেখতে কিছু কলি। ধীরে ধীরে কলিরা বড় হচ্ছিল। হঠাৎ এক সকালে দেখি, কলি নয়, ফুল। কি অবিশ্বাস্য সুন্দর ফুল! বাবাকে গিয়ে ধরলাম, কি ফুল বাবা? বাবা বলল, কলাবতী। এমন ও ফুল হয়, এমন ও নাম হয়! আমার চেতনার কূল ভাসিয়ে বাজতে থাকে কলাবতী, কলাবতী, কলাবতী। তারপর একদিন ঝিরিঝিরি বৃষ্টি নামে। গায়ে সেদিন অল্প অল্প জ্বর। মা বলে, – আজ আর দুজনের কারো, স্কুলে গিয়া কাজ নাই। আমি চাদর মুড়ি দিয়ে হাত-পা ঢেকে বিছানায় বসে থাকি, জানালার পাশে। দেখি, কলাবতী বৃষ্টিতে স্নান করে। পাতার গা বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে – টুপ – – টুপ, টুপ টুপ। ফুলের গা বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে – টুপ – – টুপ, টুপ টুপ। ঠাকু’মা এসে পাশে দাঁড়ায়। – কেমন আছ অহন? – ভালো। – জলীয় বাতাস লাগাইও না। জ্বর বাড়ব। জানালার পাল্লা অনেকটা বন্ধ হয়। একটু ফাঁক রাখা থাকে–নাতির জন্য, কলাবতীর জন্য। ছোট দু’ ভাই এবার ঘিরে আসে, – ঠাকুমা গল্প বলো।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালভোটবৈতরণী - দ্বিতীয় দফা - সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায়
২৭ এপ্রিল ২০২৪ | ২৬০ বার পঠিতএসবের মধ্যেই জানা যায়, মুখ্যমন্ত্রী হাইকোর্টকে বিজেপির দালাল বলে কেলোর কীর্তি করেছেন। বলেছিলেন আগেই, হাইকোর্ট বিশেষ রা কাড়েনি, শুধু এক বিচারপতি বলেছিলেন, এবার পঞ্চাশ হাজার চাকরি খেয়ে নেব কিন্তু। সেটায় কারোরই তেমন কিছু ক্ষতি হয়নি। বিজেপিরও কোনো সমস্যা ছিলনা। কিন্তু কার কোথায় নরম জায়গা আছে কে জানে, কোথা থেকে ব্যাপারটা গায়ে লেগে যায় বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের এবং তিনি নাকি আবার মামলা করতে চলেছেন। এবার আর শিক্ষকদের না, চাকরি খাবেন আস্ত মুখ্যমন্ত্রীর।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালবৈঠকি আড্ডায় ১৪ - হীরেন সিংহরায়
২৬ এপ্রিল ২০২৪ | ২৮২ বার পঠিতযুদ্ধের পরে এই চোদ্দ বছরের অনিশ্চিত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে কমিউনিস্ট এবং বামপন্থী দলগুলি অরাজকতা সৃষ্টি করার ফলে দেশের অবস্থা সঙ্গিন হয়ে উঠেছে । গণতন্ত্রের যুগে ব্যক্তিগত ধন সম্পত্তি রক্ষা করা সম্ভব নয় , এখন প্রয়োজন সবল নেতৃত্ব ও নতুন চিন্তা। সেটা আমি খুঁজে পেয়েছি জাতীয়তাবাদ এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক শক্তির ভেতরে । সামনের লড়াইটা বাম বনাম দক্ষিণের সম্মুখ সংগ্রাম । আমরা চাই ক্ষমতা দখল করে প্রতিপক্ষকে সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট করতে কিন্তু এই লড়াই ততদিন স্থগিত রাখতে হবে যতদিন না আমরা একচ্ছত্র ক্ষমতা আয়ত্ত না করছি। মনে রাখবেন বামপন্থীদের হাতে আপনাদের ধন সম্পদ জমি জিরেত কল কারখানা কিছুই সুরক্ষিত নয় , একবার সোভিয়েত রাশিয়ার দিকে চেয়ে দেখুন! অর্থনীতি বা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যা কিছু বরণীয় তা সম্ভব হয়েছে কোন দলীয় রাজনীতি নয় , একক ব্যক্তিত্বের ভাবনা ও চিন্তায় , নির্বাধ শক্তি ও ক্ষমতার বলে। সভাগৃহে তখনও আসীন গুম্ফ শোভিত ডক্টর হায়ালমার শাখট , যিনি পরে আবার রাইখসবাঙ্কের প্রেসিডেন্ট এবং ইকনমি মন্ত্রী হবেন । তিনি এতক্ষণ কোন কথা বলেন নি । হিটলার এবং গোয়েরিং বিদায় নিলে তিনি মুখ খুললেন “ এই ভোট যুদ্ধ জিততে গেলে , পার্টির হিসেব অনুযায়ী আমাদের অন্তত তিরিশ লক্ষ রাইখসমার্ক দরকার ( আজকের হিসেবে দু কোটি ইউরো অথবা একশ আশি কোটি টাকা) । এবার আসুন ক্যাশ কাউনটারে !” বাঘের পিঠে সওয়ার যখন হয়েছেন তখন নেমে পড়ার প্রশ্ন ওঠে না। ক্রেডিট কার্ড অনেক দূরে , চেক বই কেউ সঙ্গে আনেন নি । কিন্তু কোম্পানির পক্ষ থেকে অঙ্গীকার করার অধিকার তাঁদের ছিল – তাঁরা বিশাল প্রতিষ্ঠানের মালিক বা শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত । একের পর এক শিল্পপতি ডক্টর শাখটের চাঁদার খাতায় সই করলেন
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালকিষেণজি মৃত্যু রহস্য - পর্ব ৬ - বিতনু চট্টোপাধ্যায়
২৬ এপ্রিল ২০২৪ | ১৫৩ বার পঠিতএকদিকে ঝাড়খন্ড পার্টি। তার পেছনে কংগ্রেস। সঙ্গে পুরনো নকশালপন্থীদের প্রত্যক্ষ সমর্থন। অন্যদিকে, সিপিআইএম। তার সামনে পুলিশ। ছ’য়ের দশকের শেষে যে লড়াই শুরু হয়েছিল জমি রক্ষার এবং দখলের, তাই ১৯৭৭ সালে রাজ্যে সিপিআইএমের নেতৃত্বে বামফ্রন্ট সরকার গঠনের কয়েক বছরের মধ্যে তীব্র রাজনৈতিক লড়াইয়ে কনভার্ট করে গেল। প্রথমে জমির লড়াই, তারপর রাজনৈতিক লড়াই, আর এই দুইয়ের যোগফলে শুরু হল হিংসার রাজনীতি। হত্যা-পাল্টা হত্যা।
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাভ্রান্তিপর্বত শান্তিতীর্থ - নন্দিনী সেনগুপ্ত
২৬ এপ্রিল ২০২৪ | ২৫০ বার পঠিতএই মুহূর্তে বার বার একটা নাম শোনা যাচ্ছে। সোনাম ওয়াংচুক। অনেকেই হয়তো বলবেন যে লাদাখ নিয়ে নতুন রাজনীতির আবর্ত তৈরি হচ্ছে এই নামটিকে ঘিরে। কিন্তু যে আন্দোলন শুরু হয়েছে, সেটা সফল হলে এবং বিভিন্ন জায়গায় আরও কয়েক দশক আগে শুরু হলে হিমালয়ের প্রকৃতি কিছুটা হলেও বাঁচত।
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাসিএএ-র ফাঁদে মতুয়ারা - শান্তনীল রায়
২৫ এপ্রিল ২০২৪ | ৪৬৯ বার পঠিতবাংলার উদ্বাস্তু প্রধান এলাকাগুলিতে কান পাতলেই শোনা যায় নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে নানা গুঞ্জন। চব্বিশের লোকসভা ভোটে এই অঞ্চলগুলিতে জিততে বিজেপির মাস্টার্স স্ট্রোক এই নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ)। বিজেপি বারবার করে বলছে, সিএএ নাগরিকত্ব প্রদানের আইন, নাগরিকত্ব হরণের নয়। আর সেই আশাতেই বুক বেঁধেছে এক বিরাট সংখ্যক উদ্বাস্তু মানুষ। সিএএ-র বিষয়ে সম্যক ধারণা ছাড়াই। তবে দেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত সাহ দেশবাসীকে যেভাবে ক্রোনোলজি বুঝিয়েছিলেন, তা থেকে অতি সহজেই অনুমান করা যায় যে বিজেপির মনোবাসনা কেবল সিএএ -তে থেমে থাকবার নয়। প্রথমে সিএএ, তারপর এনআরসি (জাতীয় নাগরিক পঞ্জী)। আর যার পরিণতি হতে পারে উদ্বাস্তুদের জন্য ভয়ানক।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালদোলজ্যোৎস্নায় শুশুনিয়ায় - ৬ - সমরেশ মুখার্জী
২৫ এপ্রিল ২০২৪ | ১১৭ বার পঠিতআশির দশকে যাদবপুরের কয়েকটি ছাত্রছাত্রী শুশুনিয়া পাহাড়ে গেছে শৈলারোহণ অভ্যাস করতে - সেই ভিত্তিতে এই আখ্যান … এখন জোৎস্না উজ্জ্বল। তিনজন গভীর অভিনিবেশে তাকিয়ে আছে সুমনের দিকে। সুমন বলে চলে, "আদিমানবের আদিতেও ছিল কয়েক কোটি বছরের ক্রমবিবর্তনের ধারা। ফলে পশুসমাজের নানান প্রবৃত্তিগত বৈশিষ্ট্য আদিমানবের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছিল। বহু কোটি বছরের সঞ্চিত প্রবৃত্তিগত বৈশিষ্ট্য বা instictive characteristics মাত্র এক কোটি বছরের বিবর্তনের ফলে বিশেষ পরিবর্তিত হওয়া সম্ভব নয়। ফলে পশুসূলভ নানা প্রবৃত্তিগত বৈশিষ্ট্য বিবর্তিত মানুষের মধ্যেও সুপ্ত ভাবে রয়ে গেল..
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাবিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে…….. - সোমনাথ গুহ
২৫ এপ্রিল ২০২৪ | ৩৩৫ বার পঠিতমার্চ ও এপ্রিল পরপর দু মাসে দুজন স্বনামধন্য সমাজ ও মানবাধিকার কর্মী দীর্ঘ কারাবাসের নরক-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়েছেন। গত ৭ই মার্চ অধ্যাপক জি এন সাইবাবা প্রায় এক দশকের কারাবাসের পর নাগপুর সেন্ট্রাল জেল থেকে মুক্তি পান। এর প্রায় এক মাস বাদে ভীমা কোরেগাঁও (বিকে) মামলায় ধৃত নারী ও দলিত অধিকার কর্মী, অধ্যাপক সোমা সেন জামিন পান। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর এই দুজনের মুক্তি অবশ্যই স্বস্তিদায়ক, কিন্তু যা ঢের বেশি অস্বস্তিকর তা হচ্ছে তাঁদের গ্রেপ্তার, তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাঁদের বিচার বা বিচার না-হওয়া পুরো বিচারব্যবস্থার স্বরূপকে নগ্ন করে দিয়েছে। সাইবাবার কাহিনি বহু চর্চিত, তবুও সেটাকে আমরা ফিরে দেখব এবং কোন কারণে অধ্যাপক সোমা সেন সহ ভীমা কোরেগাঁও মামলায় ধৃত অন্যান্যদের এতো বছর কারাবাস করতে হল, এবং কয়েকজনকে এখনো করতে হচ্ছে, সেটা বোঝার চেষ্টা করব।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালশিক্ষা দুর্নীতি রায় - একটি সারসংক্ষেপ - সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায়
২৫ এপ্রিল ২০২৪ | ১০০৩ বার পঠিতমামলার গোড়া থেকে আমার করা সারসংক্ষেপ এরকমঃ ১। অযোগ্যদের সরানো নয়, পুরো প্যানেল যে বাতিল (সেট অ্যাসাইড) করতে হবে, এবং আবার অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিতে হবে, এই দাবীটা প্রাথমিক ভাবে তোলেন বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য। ২। পিটিশনারদের আইনজীবী আশিষ কুমার চৌধুরি, এরকম কোনো দাবী তোলেননি, অন্তত তুলেছেন বলে লেখা নেই। চৌধুরি বলেন, যে, দুটো অনিয়ম হয়েছে। এক, পার্সোনালিটি টেস্টের নম্বর বাকি নম্বরের সঙ্গে যোগ করা হয়নি। দুই, সিনিয়ারিটি বিবেচনা করা হয়নি। এছাড়াও তিনি কিছু খুচরো অনিয়মের কথা বলেন। সবকটাতেই র্যাঙ্ক বদলে যায়, ফলে প্রকৃত যোগ্য চাকরি নাও পেতে পারেন, বা পিছিয়ে যেতে পারে।
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাইদবোশেখির লেখাপত্তর - গুরুচণ্ডা৯
২৪ এপ্রিল ২০২৪ | ১১৮৯ বার পঠিতআমরা আপনাদের কাছে ডাক পাঠিয়েছিলাম তাদের খপ করে ধরে ফেলে, ঝপ করে লিখে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিতে। এসে গেছে তারা। আগামী কয়েকদিন ধরে রোজ দুটি-তিনটি করে তারা এসে হাজির হবে বুলবুলভাজার পাতায় - টাটকা ভাজা, গরমাগরম। পড়তে থাকুন। ভাল লাগলে বা না লাগলে দুই বা আরো অনেক লাইন মন্তব্য লিখে জানিয়ে দিন সে কথা। মন চাইলে, গ্রাহক হয়ে যান লেখকের।
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাউনিশে এপ্রিল - সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায়
২৪ এপ্রিল ২০২৪ | ২৮১ বার পঠিতমীরজাফর তো শুনে হাঁ। কুচ মানে? এ কি রাজকার্য না ফুক্কুড়ি, যে সক্কালবেলা একটু মেজাজ খারাপ হয়েছে বলে লালমুখোদের সঙ্গে একদম যুদ্ধে নেমে পড়তে হবে? রাজা-বাদশাদের খেয়ালকে একটু তোয়াজ করতে হয়—সবাই জানে, কিন্তু এই আস্ত গাছপাঁঠাটা যেমন আহাম্মক, তেমনই বদমেজাজি—রাজনীতি তো বোঝেই না, আদবকায়দাও না। নবাব না হনুমান বোঝা মুশকিল, ওদিকে ধড়িবাজি আছে দুশো আনা। কোন এক ভাগাড় থেকে তুলে এনে মোহনলালকে মহারাজা বানিয়ে মাথার উপর বসিয়েছে, সেটা আবার ওর চেয়েও এককাঠি বাড়া। সে মালটা বিষ খেয়ে অবশ্য এখন আধমরা, দরবারে নেই—এই এক রক্ষে।
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাকবিতাগুচ্ছ - বেবী সাউ
২৪ এপ্রিল ২০২৪ | ৩৭৪ বার পঠিতমানুষকে কখনো কখনো শার্দূল হয়ে উঠতে হয় / বাড়িতে তখন পোষ মানানো হচ্ছে / কুকুরের বাচ্চা / পোষ্য এবং পোষক দু'জনেই লোভনীয় / খোঁড়া পা নিয়ে আমার বিপ্লবী জেঠু / শার্দূলকে ভেবে বসছে কুকুর / কুকুর নিজেকে জেঠু ভেবে / সেজে উঠছে অযোধ্যায় যাবে বলে / পোষ্যদের খাদ্য প্রয়োজন / প্রয়োজন সঠিক সময়ে / সঠিক সমস্যা বোঝা / একটা হাড়ের লোভে শার্দূল ছুটছে / পেছনে পা খুঁড়িয়ে জেঠু / হাড় এবং / লোভ এবং / খোঁড়া পা / হো হো করে হেসে উঠছেন / আমাদের প্রণম্য / সন্তোষ রাণা
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাইদ বৈশাখ মানে মা - ইমানুল হক
২৪ এপ্রিল ২০২৪ | ১২৪ বার পঠিতসকাল সকাল একটা আম পাই। তার গায়ে সদ্য পাড়া আঠার গন্ধ। যাঁরা এই গন্ধ জানেন, তাঁরা মানবেন, কীভাবে মাতাল করে তোলে এই গন্ধ। কোনও কৃত্রিম গন্ধ একে প্রতিস্থাপন করতে এখনও পারে নি। অন্তত আমার জানা মতে। সোঁদা মাটির গন্ধ একেক জায়গায় একেক রকম। একেকটা আমের জাতের একেক রকম গন্ধ। কিন্তু আঠার গন্ধ বোধহয় এক। নাহলে ৬-১০ বছরের এক বালকের নাকে স্মৃতিতে ডুব মেরে থাকা গন্ধ কীভাবে আজ ঝড় তুলে দিলে প্রৌঢ় মনে! মায়ের গায়ের গন্ধ যেমন শিশুকে চিনতে শেখায়, তেমন আমের গন্ধ সাবালকত্বকে। একা একা আম পাড়া ঢিল মেরে, গুলতি ছুঁড়ে, আঁকশি দিয়ে, আরেকটু বড় হলে গাছে উঠে--সাবালকত্বের লক্ষণ। বয়স নয়, আনন্দের। পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়া যেমন আরেক আনন্দ। আনন্দের কী কোনও ব্যাঙ্ক আছে? এআই কী এই আনন্দ কোনও দিন দিতে পারবে? পারবে লিখতে সহজ সহজ সুখ আর অতি সরল আনন্দের গন্ধের কথা। মায়ের হলুদ মাখা আঁচলের, গায়ের গন্ধ কি দিতে পারবে কোনও রোবট?
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাবুড়োশিবতলা - পায়েল চট্টোপাধ্যায়
২৪ এপ্রিল ২০২৪ | ২২২ বার পঠিতজলের মধ্যে গোলা নীল রংটা নিজের গালে ঘষছে সুদাম।ঘষতে ঘষতে একটা মুখ মনে পড়ছে। সিনেমার মত। তারপর হঠাৎ নিজের আয়না দেখা মুখটা মনে পড়েছে। শুষ্ক, খড়খড়ে। একটা যন্ত্রণা ঠেলে উঠে আসছে। রংটা জোরেই ঘষে দিচ্ছে ও। হঠাৎ ব্যথায় কঁকিয়ে ওঠে। ওঠারই কথা। তবে গালের ব্যথায় নয়, মনের ব্যথায়। গৌরী যদিও ইচ্ছে করে মারেনি। সুদাম এক বুক কাদার মধ্যে একেবারে পা ডুবিয়ে সিনেমার হিরোদের কায়দায় গৌরীকে কথাটা বলতে চেয়েছিল। "এখুনি আন্ধার নামবে, তুই পাড়ার ওই ম্যাদামারা ছেলেটা না! কথা বলার মুরোদ নেই, এমন গায়ের কাছে এসেছিস কেন? দেখছিস লা কাজ করতিছি ক্ষেতে! যা এখান থেকে!" কথাগুলো বলেই কোদালটা হাতে তুলে নিয়েছিল গৌরী। কাজ করার জন্যে। সুদাম এত কাছে এসে পড়েছিল যে কোদালের বাঁটের আঘাত লাগতে একটুও দেরী হয়নি।
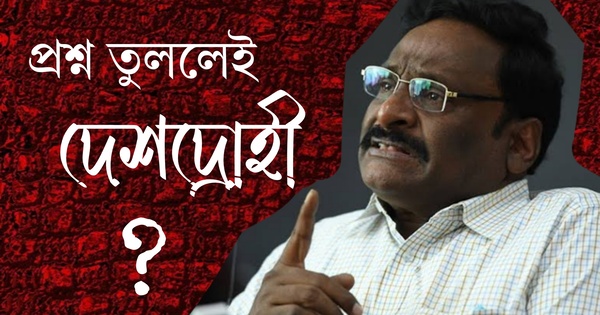 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাশাসককে প্রশ্ন করলেই দেশদ্রোহিতার তকমা! - ডঃ দেবর্ষি ভট্টাচার্য
২৩ এপ্রিল ২০২৪ | ৩০১ বার পঠিতগোকারাকণ্ডা নাগা (জি এন) সাঁইবাবা। পোলিও রোগে আক্রান্ত হয়ে শৈশবকাল থেকেই শারীরিকভাবে পঙ্গু। ফলস্বরূপ, পাঁচ বছর বয়স থেকেই হুইল চেয়ার ছাড়া চলাচলে অক্ষম। মানুষের অধিকার রক্ষার আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী। বিদগ্ধ লেখক। রাষ্ট্রীয় দমন পীড়নের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদী। রাষ্ট্রীয় মদতে সংগঠিত ‘অপারেশন গ্রীনহান্টের’ কট্টর সমালোচক। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ রামলাল আনন্দ কলেজের ইংরাজি বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক। বর্তমান বয়স ৫৭ বছর। শারীরিকভাবে ৯০ শতাংশ প্রতিবন্ধী এবং প্রায় চলৎশক্তি রহিত। আত্মগোপন করে থাকা মাওবাদীদের লেখাপড়া শিখিয়ে রাষ্ট্র বিরোধী হিংসাত্মক কার্যকলাপে প্ররোচিত করার অভিযোগে ২০১৪ সালের ৯ই মে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালভোটুৎসবে ভাট - লক্ষ্মীবাবুর নকলি সোনার টিকলি - সমরেশ মুখার্জী
২৩ এপ্রিল ২০২৪ | ৩৭২ বার পঠিতদুঃসময়ে ছোট্ট স্ফূলিঙ্গও জোগায় অবান্তর রচনা লেখার প্রয়াসে আত্মমগ্নতায় ডুবে থাকার দাওয়াই। লেখার উপাদান সংগ্ৰহকালে জানা যায় নানা চমকপ্রদ বা আনন্দময় তথ্য। পলায়নবাদীরা এভাবে এড়িয়ে থাকতে চায় বিষাক্ত বর্তমানের অভিঘাত।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালচান রাত! - মহম্মদ সাদেকুজ্জামান শরিফ
২৩ এপ্রিল ২০২৪ | ৩৮০ বার পঠিতযাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আছে তাঁদের আমাদের মতো এমন সৌখিন চিন্তা ভাবনা করার ফুসরত নাই। শেষ মুহূর্তে কেনাকাটার হিড়িক লাগে কেন জানি। কিছু মানুষই আছে যারা কোন অজ্ঞাত কারণে সারা মাস কেনাকাটার আশপাশ দিয়েও যেতে রাজি না। প্রথম থেকেই নিয়ত পাকা যে তিনি যাবেন চান রাতেই! কেউ কেউ তো এমনও বলে যে চান রাত ছাড়া শপিং করে মজাই পাওয়া যায় না। কেউ চান রাত ছাড়া আবার ইদ শপিং হয় না কি? এমন প্রশ্নও করে। তো এই খদ্দেরদের জন্য চান রাতে চলে ভোর পর্যন্ত জমজমাট কেনাকাটা। রাত একটা দুইটা তিনটা যেন সন্ধ্যা রাত! ঢাকায় কোন দিন ইদ করা হয়নি। কিন্তু বন্ধুদের অনেকের কাছেই শুনেছি যে ঢাকায় চান রাতের জৌলুসের সাথে কোন কিছুর তুলনাই হয় না। দেড় দুই কোটি মানুষ চান রাতের আগে ঢাকা ছেড়ে চলে গেছে। ঢাকা হাঁফ ছেড়ে গা ঝাড়া দিয়ে দাঁড়িয়েছে। যারা বের হচ্ছে তারা চলে ফিরে, দেখে শুনে, কিনে না কিনে আলাদা সুখ পাচ্ছে। ঢাকার জ্যাম ঘাম গরম যে দেখছে সে চান রাতে না থাকলেও অনুমান করতে পারে যে কতটা হালকা লাগছে সবার এই দিন!
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাসুর - অনুরাধা কুন্ডা
২৩ এপ্রিল ২০২৪ | ৩৪৭ বার পঠিতফোন বেজে উঠতেই শ্যামশ্রীর গলা ভেসে এলো। ছটফটে, তরতরে শ্যামশ্রীর গলা নয়। রাগী, কড়া শ্যামশ্রীর গলাও নয়। চটপটে, স্মার্ট নয়। একটু ভেজা ভেজা। দরদী। নরম। ত্রিলোকেশের এখন ঠিক যেমন দরকার তেমনটি। যখন যেমন দরকার, তেমনটি। যখন খোলামেলা চাই তখন খোলামেলা। যখন লাজুক চাই তখন লাজুক। যখন লাস্য চাই তখন লাস্য। এইভাবেই। ঠিক এইভাবেই প্রোগ্রামড করা আছে। কন্ঠস্বর, চলাফেরা, ওঠাবসা, ফুড হ্যাবিট, যৌনতা , এমনকি পটি টাইমিং পর্যন্ত। শ্যামশ্রী না। শ্যামশ্রীর ক্লোন। শ্যামশ্রী দত্তগুপ্ত টু। হাইট পাঁচ পাঁচ। রঙ মাজা। চুল স্ট্রেইট। গোল্ডেন হাইলাইট। অবিকল ওরিজিনাল শ্যামশ্রী।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালভারত -- শেষ ধ্বংসের সন্ধিক্ষণে - Partha Banerjee
২২ এপ্রিল ২০২৪ | ৬৩৯ বার পঠিতপার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক বিশ্লেষণমূলক গ্রন্থ "ভারত -- শেষ ধ্বংসের সন্ধিক্ষণে" (অভিযান পাবলিশার্স, মার্চ ২০২৪)'এর একটি সমালোচনা।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালফারাও-এর দেশে কয়েকদিন - পর্ব ৯ - সুদীপ্ত
২২ এপ্রিল ২০২৪ | ১৯৬ বার পঠিতলাক্সর মন্দির থেকে কার্নাকের মন্দির পর্যন্ত ছিল একটি সুপ্রাচীন রাস্তা, যার নাম ‘Alley of Sphinxes’ বা ‘Avenue of Sphinxes’। এই রাস্তাটি ছিল প্রায় দু-কিলোমিটার দীর্ঘ। আমরা বাস থেকেই দেখলাম সেই রাস্তা আর তার দুপাশে স্ফিংক্স-এর সারি, যদিও অধিকাংশ-ই ভাঙা। বাসের একদিকে রয়েছে লাক্সর মন্দির, অন্যদিকে কার্নাক। আর আমাদের বাস এই অ্যাভিনিউ-এর উপর দিয়ে একটি সেতু পার হয়ে এগিয়ে চলল। এই স্ফিঙ্কস-গুলির কিছু তৈরী হয়েছিল ফারাও তুতানখামুনের আমলে, কিছু তৃতীয় আমেনহোটেপের আমলে আর বাকিটুকু ফারাও প্রথম নেকতানেবো-র সময়ে। প্রায় মিনিট পনেরো পরে আমরা এসে দাঁড়ালাম কার্নাক মন্দিরের পার্কিং-এ।
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাসাদা খাম - দীপেন ভট্টাচার্য
২২ এপ্রিল ২০২৪ | ৫৮৪ বার পঠিততার স্ত্রী তাকে ফিরে আসতে না করেছিল, অনেক অনুনয় করেছিল, কিন্তু সে শোনেনি। বিমানবন্দরে নামামাত্রই তাকে আটক করা হয়েছিল। নিয়ে আসা হয়েছিল রাজধানী থেকে বহু দূরে এই বন্দিশিবিরে। সে জানত এরকমই হবে। সকালে তাকে নিয়ে যাওয়া হতো অন্য একটি ঘরে, পার হতে হতো একটি করিডর, এক পাশে দেয়াল, অন্য পাশে পর পর আটটি কামরা, এর মধ্যে একটি ছিল তার। কিন্তু সেটা সে বুঝতে পারত না, কাপড় দিয়ে বাঁধা থাকত চোখ। ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে লাগলে বুঝতে পারত বাড়িটি থেকে সে বের হয়েছে। এর পরে ত্রিশটি পদক্ষেপ, অন্য একটি বাড়িতে ঢোকা। সেখানে একটি ঘরে তাকে চেয়ারে বসিয়ে চোখের বাধন সরিয়ে নেওয়া হতো। মিনিট দশেক অপেক্ষার পর আসত কমিসার। প্রথম দিন সে জিজ্ঞেস করেছিল, ‘আমি কে আপনি জানেন?’ কমিসার বলেছিল, ‘আমি জানি আপনি জনগণের শত্রু, এটুকুই আমার জন্য যথেষ্ট।’ বেশি জানা কমিসারের জন্য ভালো নয়।
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাগল্পসমগ্র’ (২০২২) প্রথম খণ্ড (উপল মুখোপাধ্যায়) - পুরুষোত্তম সিংহ
২২ এপ্রিল ২০২৪ | ৩৪৫ বার পঠিতবিজ্ঞাপনের মোহিনী মায়া, সংবাদের আলো-আঁধারি ভাষা, কুঞ্ঝটিকা, বাজার ধরার কৌশল সমস্ত মিলিয়ে যে ফাঁদ তার প্রগাঢ় ভাষ্য উপল নির্মাণ করে নেন। সেই নির্মাণে গপ্প হিসেবে উপলকে অনেক সময়ই বাস্তবের আড়ালে চলে যেতে হয়। বাস্তবকে ধরে অপ্রচ্ছন্ন বাস্তবের প্রতিমূর্তি গড়ে তোলেন। সেই অপ্রচ্ছন্ন বাস্তবের ছায়ামূর্তির মধ্যেই বাস্তবের প্রতিমা লুকিয়ে আছে। সেখানে পাঠক বাস্তবকে আবিষ্কার করবেন বা প্রত্যাখ্যান করে অধিবাস্তবের স্বরকে দেখবেন সেটা পাঠকের প্রত্যাশার উপর ছেড়ে দেন। পাঠকের ভাষ্যে তা শিল্প হতেও পারে আবার নাও হতে পারে। সেসব নিয়ে উপলের কোনো মাথা ব্যথা নেই। তিনি শিল্প বা না-শিল্প বৃত্তের ভাবনায় পাঠককে যে মাতিয়ে রাখতে পারেছেন সেটাই তাঁর সার্থকতা। হ্যাঁ তিনি রীতিমতো পরীক্ষা নিরীক্ষা করে যান। গদ্যসেতু ধরে ভাবনার তরঙ্গ বিচ্ছুরণে পাঠকের মস্তিষ্কে একাধিক বিরোধাভাসের জাল বুনে দিতে চান। সেখান থেকে পাঠক বাস্তবের সত্যে ফিরুক বা বাস্তবকে অস্বীকার করে শিল্পের সত্য বুঝে নিক।
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাসিন্দবাদের গল্প ছড়ানো ছাদে - সুকান্ত ঘোষ
২২ এপ্রিল ২০২৪ | ২৪৯ বার পঠিতগলির শেষ প্রান্তে একসময় বাজত সুরের রজনীগন্ধা গ্রীষ্মের ক্লান্ত দুপুরে, শীতের মিঠে রোদে ছাদে উঠে মেলে দিত ছাপা কাপড়, ছড়িয়ে যেত রেক্সোনা সাবানের চেনা গন্ধ কৈশোর চাইত আরো একটু গায়ের কাছে যেতে ঘেঁষে যেত ঝুঁকে আসা গাব গাছের পাতা কাটা কাটা ছায়ায় বসে ফিসফিস করে কানের কাছে কেউ বলত নিষিদ্ধ গল্প – একের পর এক শীতের চাদরের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসা দুধ সাদা হাতে আলতা চুঁয়ে পড়া দেখতে বলত মিঠে ফিনফিনে গলা বলত চাদরে জড়িয়ে রাখা আছে সিন্দবাদের গল্পের ঝুলি আলাদিন হবার প্রলোভন দেখাত দুপুরের ছাদ –
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাকবিতাগুচ্ছ - মণিশংকর বিশ্বাস
২২ এপ্রিল ২০২৪ | ৫৫৪ বার পঠিতযারা ভোর-ভোর উঠে স্বাস্থ্যচর্চা করে পার্কে দৌড়ায় ঠিক করে দেখলে আসলে তারা মৃত্যুভয়ে দৌড়ায় একথা লিখেই মনে পড়লো— তুমিও তো ঠিক করে দ্যাখোনি কখনো আমি কেন এভাবে দৌড়ে গেছি তোমার দিকে পড়ে গিয়ে, হোঁচট খেয়ে, আবার হেঁটে গেছি এক বর্ষা আগুনের ভিতর দিয়ে শুধুই তোমার পাবার জন্য!
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাপুস্তক সমালোচনা : কাদামাটির হাফলাইফ (ইমানুল হক) - প্রদীপ দাস
২১ এপ্রিল ২০২৪ | ২২২ বার পঠিতবইটি পড়া শেষ করে মাথায় একটা কথা ঘুরপাক খাচ্ছে এবং মনে হচ্ছে যে এই বইটি না পড়ে মরে গেলে বড্ড অন্যায় হয়ে যেতো। প্রায় প্রতিটি অধ্যায়ের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বারবার মনে হয়েছে যে এই বই আমার জীবনের ফেলে আসা দিনগুলোকে মনে করে লেখা হয়েছে। এই বই আমার একান্ত নিজস্ব জীবন দলিল বললেও হয়তো অত্যুক্তি হবে না। ... ...জীবন মানেই উৎসব, জীবন মানেই সম্ভাবনা। আপনার লেখাগুলো প্রতি মুহূর্তে সেই জীবনেরই জয়গান গেয়েছে। কাদামাটির হাফলাইফ জীবন থেকে শিক্ষা নিয়েই জীবনকে উপলব্ধি করতে শেখাবে, এই বিশ্বাস জারি থাকল।
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাএই জীবনের তিনকাহন (শুক্লা রায়) - মালিনী সিদ্ধান্ত
২১ এপ্রিল ২০২৪ | ৫৫৯ বার পঠিতএই জীবনের তিনকাহন-এর প্রথমপর্ব, ‘বাপের বাড়ি’। লেখিকার জন্ম ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে। রাসবিহারী অ্যাভিনিউ-এ বাড়ি। ঠাকুরদা, ঠাকুমা, বাবা, জ্যাঠা, কাকা, পিসি সকলে মিলে বিশাল এক যৌথ পরিবার। চন্দননগরে সংস্কৃত টোল পণ্ডিতের বংশগত জীবিকা ছেড়ে শিক্ষা-চাকরির জন্য ঠাকুরদার কলকাতায়ন। তারপরে কলকাতায় বাড়ি বানিয়ে পাকাপাকি ভাবে বসবাস। বাবা-কাকা-জ্যাঠারা স্ব-স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। কেউ ইঞ্জিনিয়ার, কেউ বা আইনজীবী। বাড়ি ভর্তি ভাই-বোনেরা, আর আছেন গোপালজিউ। সেইজন্য বাড়িতে আমিষ খাবারের প্রচলন নেই। ভাই-বোনেরা মিলে বাড়িটাকে পুরো মাতিয়ে রাখে। কখনও থিয়েটার, কখনও হাতে-লেখা পত্রিকা প্রকাশ, আবার কখনও বা নিখাদ দুষ্টুমি। সঙ্গে বিজয়া, দোল, ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার মতো চিরাচরিত উৎসব পালন তো লেগেই আছে। সেখানেও অবশ্য পারিবারিক বৈশিষ্ট্যের বিশেষ কিছু স্বাক্ষর আছে। অন্দরের অন্তর লেখিকার লেখায় এক নিরবচ্ছিন্ন চিত্রপটে ধরা দিয়েছে।
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাক্যালিডোস্কোপে দেখি - জীবন নাটক - অমিতাভ চক্রবর্ত্তী
২০ এপ্রিল ২০২৪ | ৪১৫ বার পঠিতরবিবুড়োর ডাকঘর থেকে একটা ছোট অংশ ছিল আমাদের পাঠ্যবইয়ে, অমল ও দইওআলা শিরোনামে। দিদিমণিরা সেটাই বেছে নিলেন মঞ্চস্থ করার জন্য। সম্ভবত: প্রচুর পটর-পটর করার যোগ্যতায় আমি মনোনীত হলাম অমল-এর ভূমিকায়। চতুর্থ শ্রেণীর এক শ্রীমান হল দইওআলা।সেই প্রথম জেনেছিলাম রিহার্সাল কাকে বলে। শেষ ক্লাস-এর পরে শুরু হত। ভাল লাগত, তবে একটু ক্লান্ত হয়ে যেতাম – আমার তো কবে সব মুখস্ত হয়ে গেছে, ভাব ভঙ্গী সহ! দিদিমণিরা মাঝে মাঝে আলোচনা করতেন কেমন করে মঞ্চসজ্জা করলে বা আর কি কি করলে নাটকটা একেবারে সত্যির মত করে তোলা যায়। সেই সব কিছু কিছু শুনে আমার ধারণা হয়েছিল যে আসল অনুষ্ঠানের দিন আমাকে দইওআলা ছেলেটির হাত দিয়ে একটা সত্যি দই-য়ের ভাঁড় দেওয়া হবে। আমার কাছে নাটকের আসল আকর্ষণ ছিল সেটা এবং সেই নিয়ে ভিতরে ভিতরে খুব উৎফুল্ল থাকতাম।
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাপলাণ্ডু সংহিতা - নন্দিনী সেনগুপ্ত
২০ এপ্রিল ২০২৪ | ৪৪৭ বার পঠিতএকটা নধর আকারের গোটা পেঁয়াজ, পান্তাভাতের থালার পাশে। এই স্বপ্নটা বিলাস ক’দিন ধরেই দেখছে। আসলে এখন গোটা একটা পেঁয়াজ একবেলায় কে আর খেতে পাবে? অর্ধেক বা সিকিভাগ বরাদ্দ, যা দাম বাড়ল… কিছু করার নেই। বাদ চলেও যেতে পারে একদম। তখন শুধু লঙ্কার আচার দিয়েই… বউ দু’আঙুল দিয়ে যেভাবে সিঁদুর পরত, সেভাবে একটিপ লাল লঙ্কার আচার কৌটো থেকে তুলে নেবে সে।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালদোলজ্যোৎস্নায় শুশুনিয়ায় - ৫ - সমরেশ মুখার্জী
২০ এপ্রিল ২০২৪ | ১২১ বার পঠিতআশির দশকে যাদবপুরের কয়েকটি ছাত্রছাত্রী শুশুনিয়া পাহাড়ে গেছে শৈলারোহণ অভ্যাস করতে - সেই ভিত্তিতে এই আখ্যান … ঈশু বলে, "দ্যাখ জেঠু, এসব কথা বলতে কিন্তু আমারও খারাপ লাগছে যেমন লাগছে তোর শুনতে। কিন্তু এসব তো বাস্তব সত্য। হয়তো ভবিষ্যত সমাজে এমন অসাম্য, অবিচার থাকবে না। তখন আমাদের মতো কেউ এমন আলোচনা করবে কেবল অতীত বিচ্যূতি পর্যালোচনার জন্য। তবে আমার জীবদ্দশায় তেমন দিন আমি দেখে যেতে পারবো বলে মনে হয় না..
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাবিপ্লবের আগুন - কিশোর ঘোষাল
২০ এপ্রিল ২০২৪ | ৩২৮ বার পঠিতডামল মায়ের দিকে তাকিয়ে চোক নাচিয়ে মুচকি হেসে বলল, “আমার বাপ তোরে কোনদিন কয়েচিল, কোতা যায়, কী করে? শুধোলি কইত “আজকাজ”। আমারও সেই “আজকাজ”। তয় কোন আজা, কেমন আজা, তার আনি কে, সেটি বুলতে পারবনি। আমার বাপও ওই কাজই করত, সে কতা তুই, জানিস। তুই যে ওই ভুঁড়ো-শেয়াল নাদুটাকে ঢিট করেছিলি, সে কতাটা জেনেই বাপ আমার, তোকে-আমাকে ছেড়ে লিশ্চিন্তে বাইরে বাইরে কাজে ফিরতে পারত। তুই আমার বৌ হুলটার বুকেও অমন বল এনে দে দিকিন, মা”। “নে, নে আমারে আর বেশি ভালাই বুলোতি হবে নি। আজকাজ করিস না কি ছাইপাঁশ করিস, বুজি না বাপু। আজার সঙ্গের নোকেরাও দেকেচি – কেমন সোন্দর সাজপোশাক পরে, মাথায় পাগ বাঁধে, গলায় এতএত সোনার হার পরে। তোদের বাপ-ব্যাটার মতো অখদ্দ্যে চেহারার কাউকে কোনদিন দেকিনি”। ডামল অবাক হয়ে বলল, “তুই আবার আজা-আনিদের কবে চাক্ষুষ করলি, মা?”
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাসীমানা - ৪৫ - শেখরনাথ মুখোপাধ্যায়
২০ এপ্রিল ২০২৪ | ১১৯ বার পঠিতনজরুল এবারেও কোন জবাব দেয়নি। সামনে একটা দড়ি-বাঁধা ফাইল, সে খোলে সেটা। একেবারে ওপরের কাগজখানা হাতে তুলে নেয়, যা লেখা আছে কাগজে তাতে চোখ বোলায় একটু, আবার রেখে দেয় ফাইলে। ঘরে আরেকবার ঢোকে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ; এবার একটু দ্রুততর, বলে, মানুষকে কন্ট্রোল করতে পারছে না পুলিশ, ধাক্কাধাক্কি হাতাহাতি চলছে। এবার ধারাবিবরণী একটু বন্ধ করে তোমার কবিতাটা পড়া দরকার। কোনরকমে এই কথাগুলো বলে নিজের একটা হাত সে বাড়িয়ে দেয় নজরুলের দিকে। নজরুল নৃপেনের হাতটা ধরে, ফাইলটাও সঙ্গে নেয়। ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে স্টুডিওর ভেতরে যায় ওরা, পাশাপাশি দুটো চেয়ারে বসে। যে দু'জন মাইকের সামনে বসেছিল, দুজনেরই কানে একটা করে ইয়ারফোন। শবযাত্রার সঙ্গে অতি ধীরগতিতে রেডিওর গাড়ি চলতে চলতে শবযাত্রার যে সংক্ষিপ্ত ধারাবিবরণী সরাসরি পাঠিয়ে দিচ্ছে রেডিওর স্টুডিওয়, ইয়ারফোনে তা শুনে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সম্প্রচারযোগ্য ভাষায় তার তাৎক্ষণিক অনুবাদ করে দুজন ঘোষকের একজন বেতারে তা পাঠিয়ে দিচ্ছে তার নিজস্ব কণ্ঠস্বরে। দ্বিতীয় জন, এখন যে শুধু ইয়ারফোনেই মনোযোগী, চেয়ারে বসে-থাকা নজরুল-নৃপেনের দিকে সে হাত তুলে ইঙ্গিত করতেই নৃপেন কাজির হাতে হাত রাখে। কাজি একটুও সময় নষ্ট না করে পড়তে শুরু করে:
- আরও বুলবুলভাজা ... আরও হরিদাস পাল ...
-
গুরুচণ্ডা৯-র গ্রাহক হোন
কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে গুরুচণ্ডা৯-র গ্রাহক হোন। গুরুচণ্ডা৯তে প্রকাশিত লেখাগুলি পেতে চাইলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যুক্ত হোন, অথবা, আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলটির গ্রাহক হোন।
- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই
- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... )
(লিখছেন... Sara Man, প্যালারাম, যদুবাবু)
(লিখছেন... Shuvendu Pal, Subhadeep Ghosh, হীরেন সিংহরায়)
(লিখছেন... হীরেন সিংহরায়, Kishore Ghosal, হীরেন সিংহরায়)
(লিখছেন... মৌসুমী , স্বাতী রায় , রমিত চট্টোপাধ্যায়)
- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন
(লিখছেন... )
(লিখছেন... রমিত চট্টোপাধ্যায়, দ, kk)
(লিখছেন... দ)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... )
- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... )
(লিখছেন... রঞ্জন , kk, Ranjan Roy)
(লিখছেন... পাপাঙ্গুল)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... jsl, মনমাঝি)
- কি, কেন, ইত্যাদি
- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...
- আমাদের কথা
- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...
- বুলবুলভাজা
- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...
- হরিদাস পালেরা
- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...
- টইপত্তর
- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...
- ভাটিয়া৯
- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...