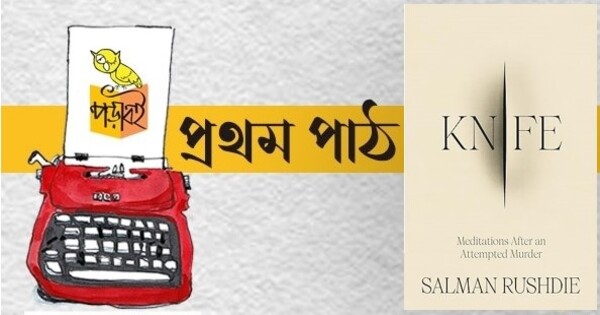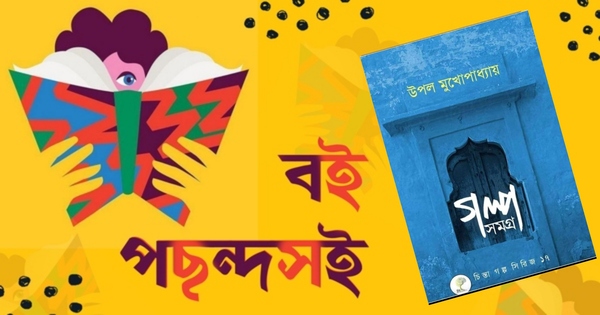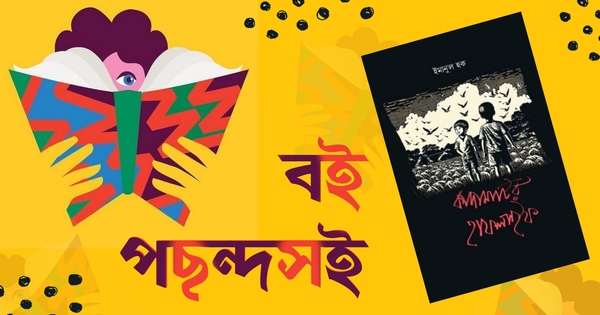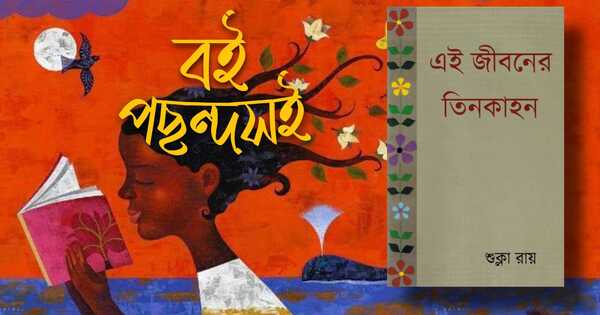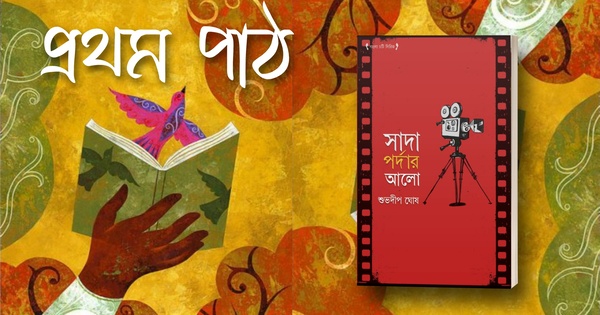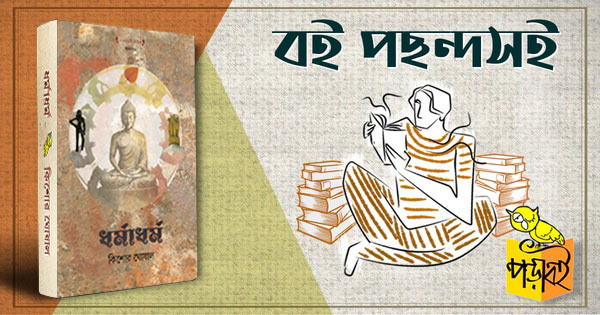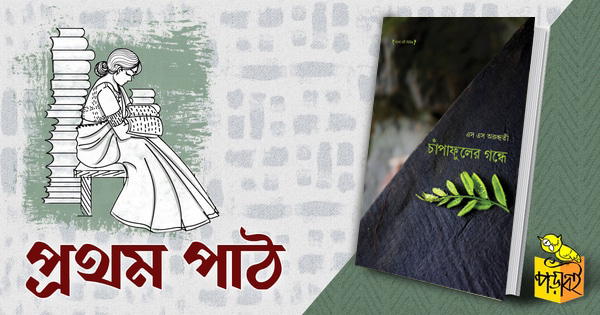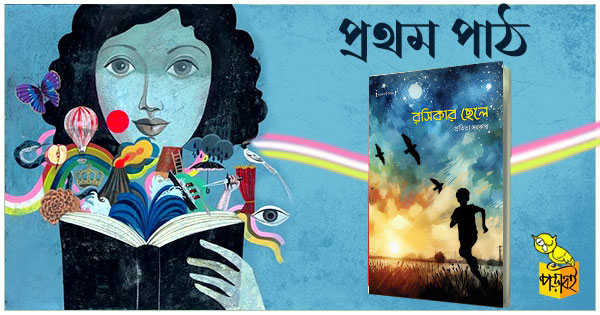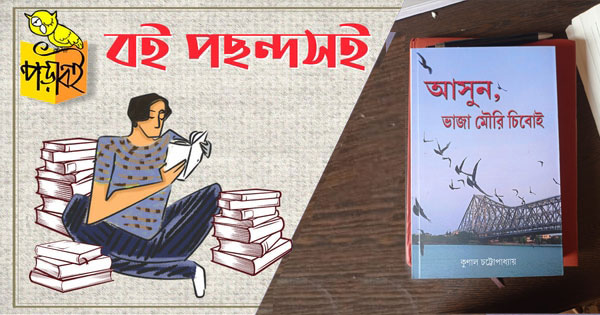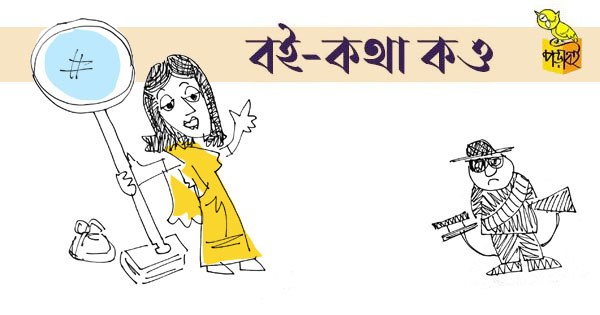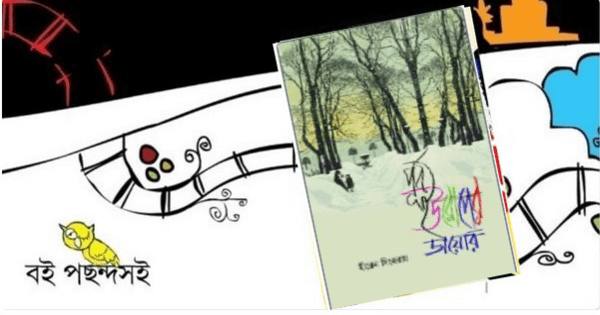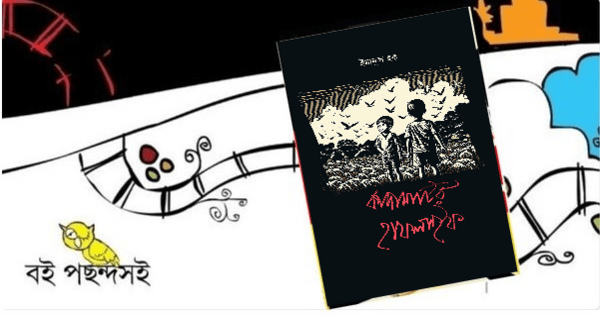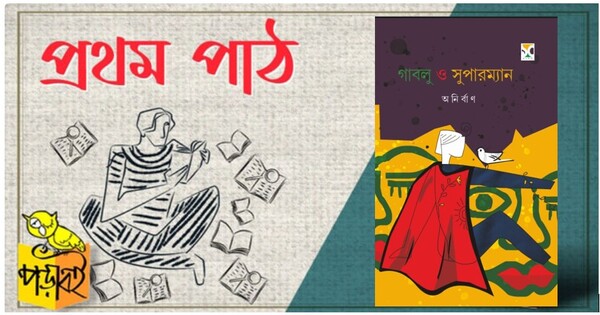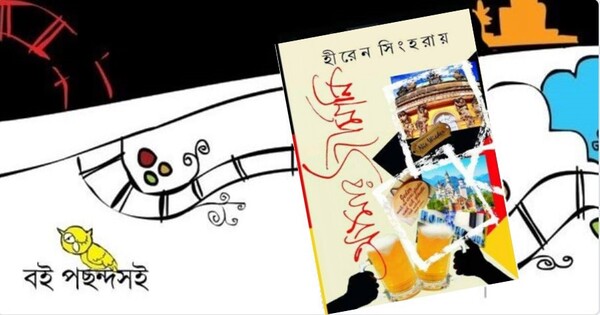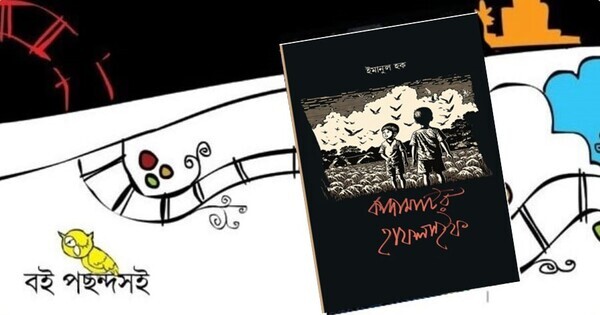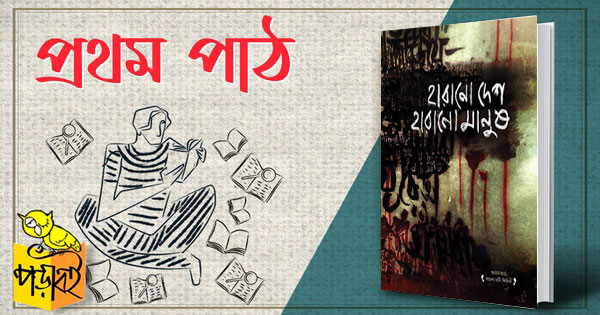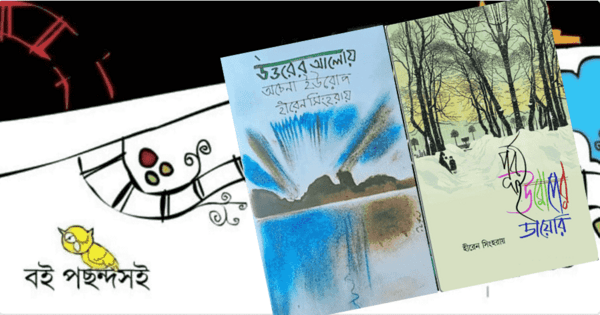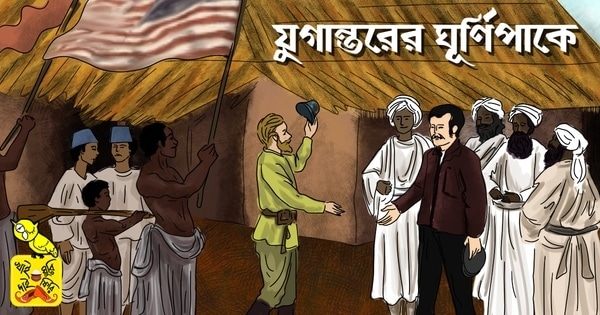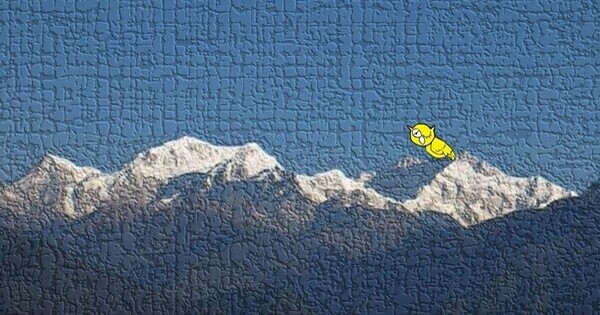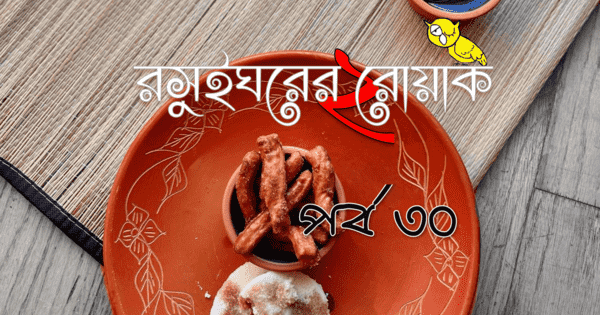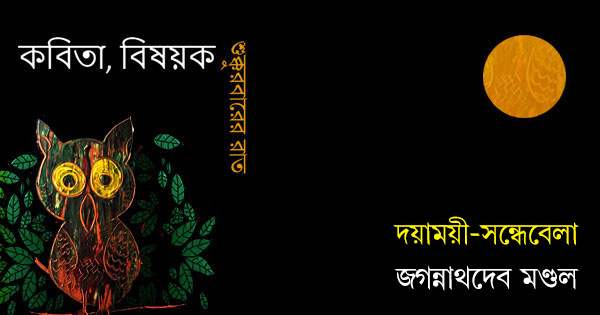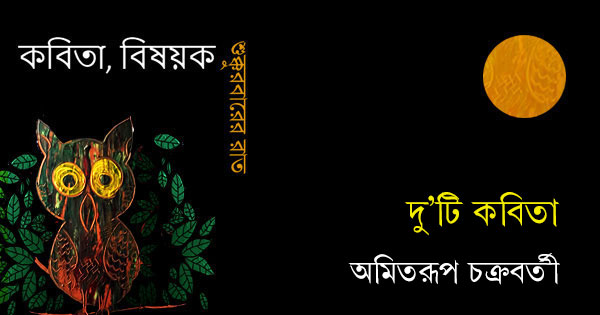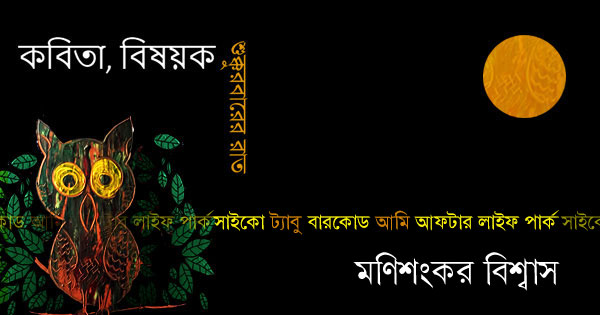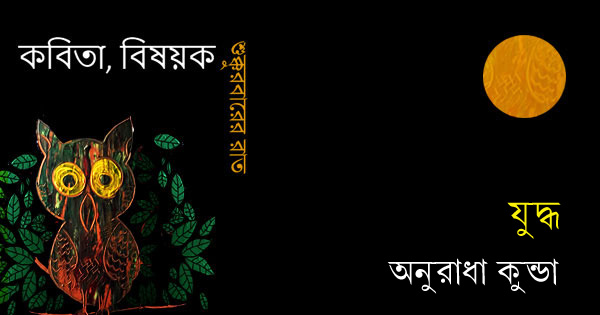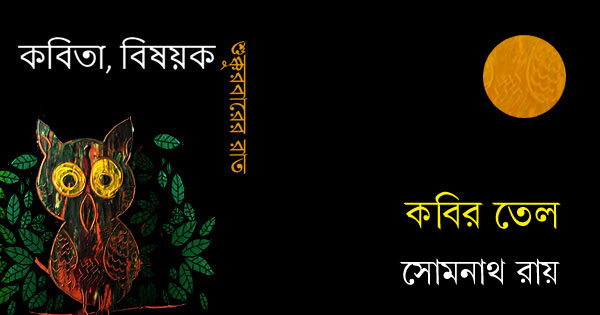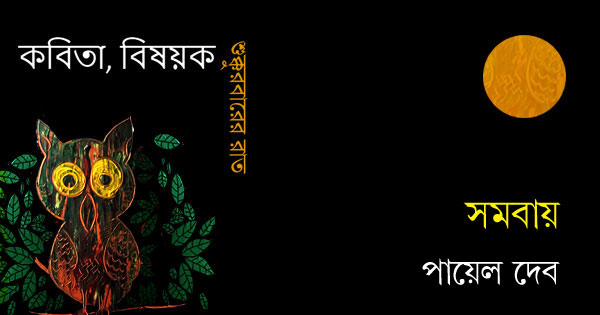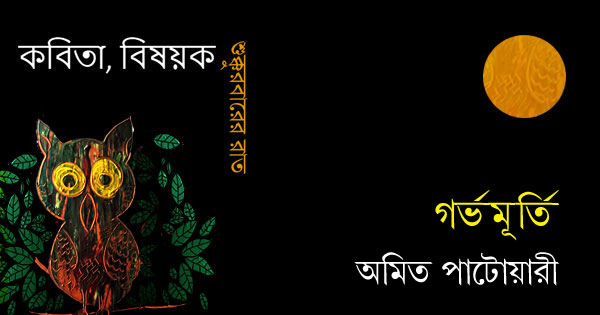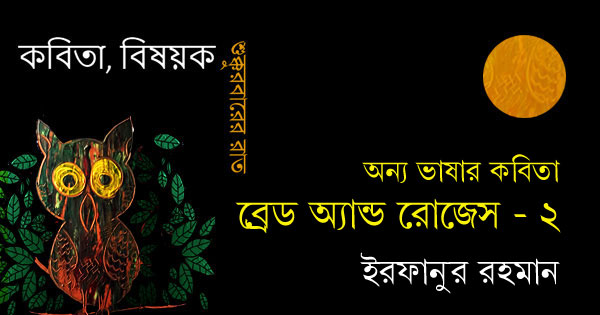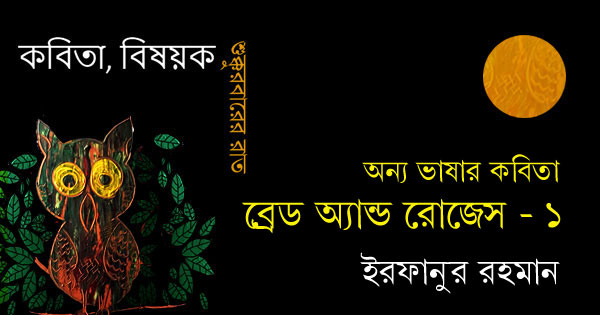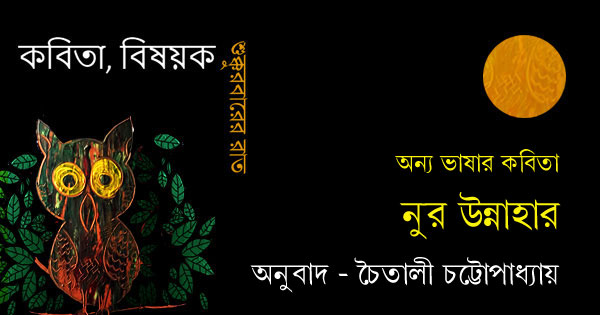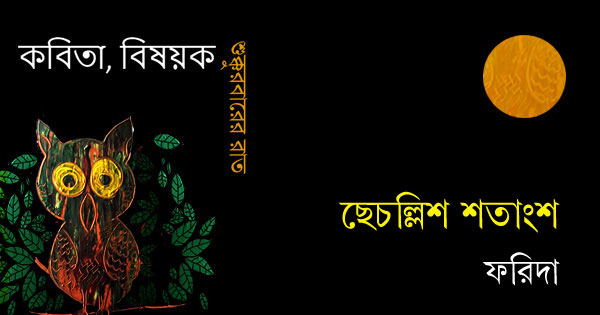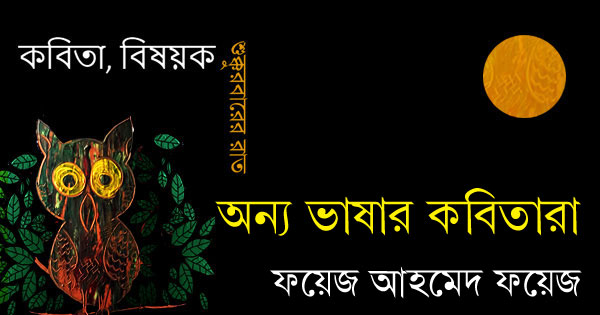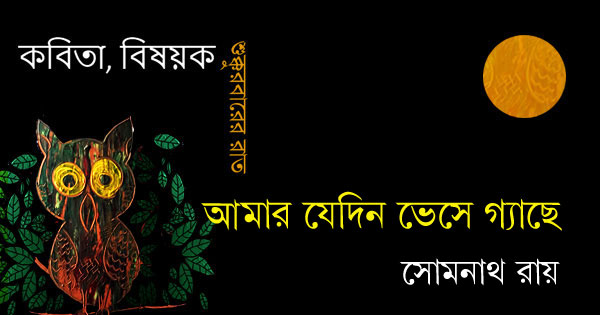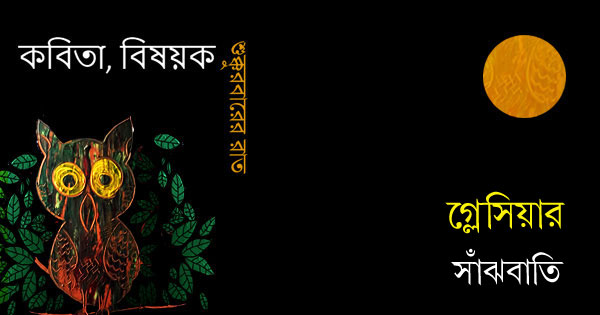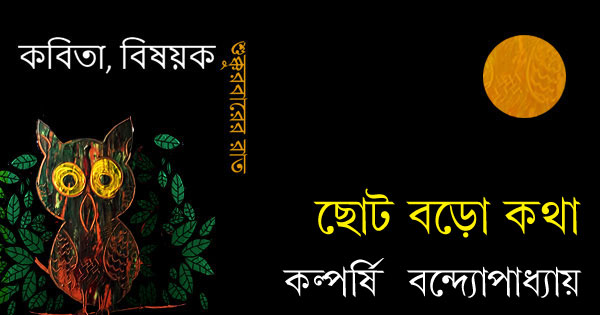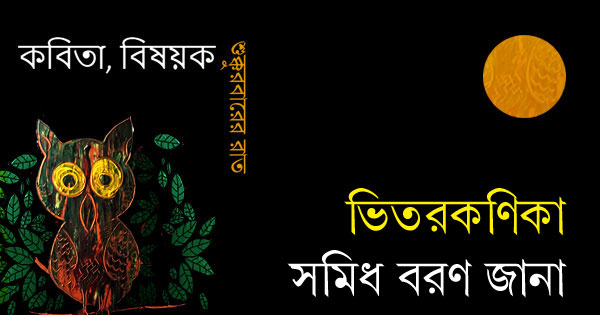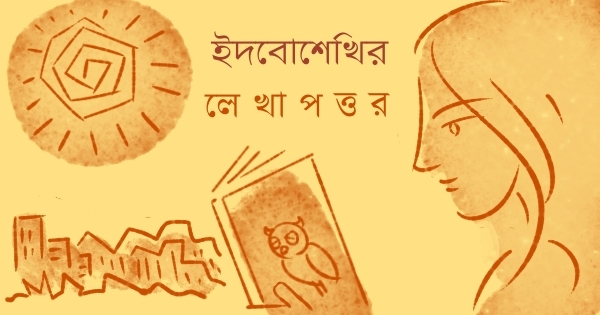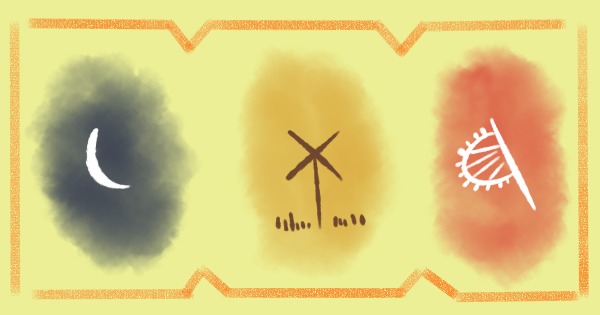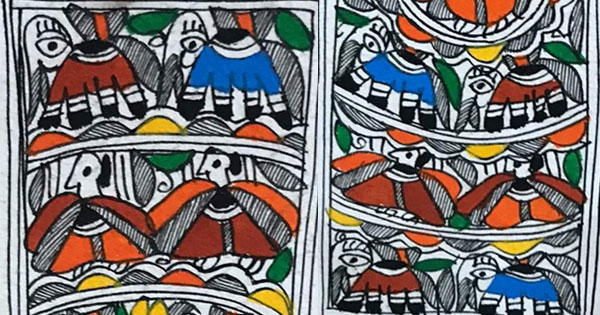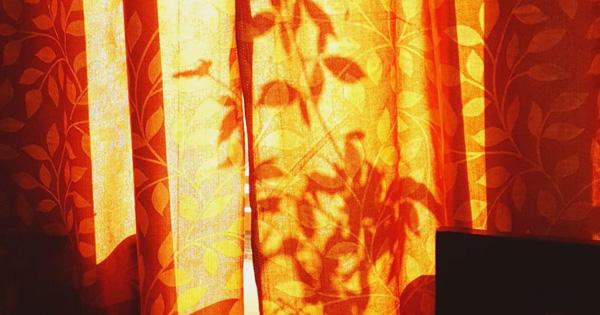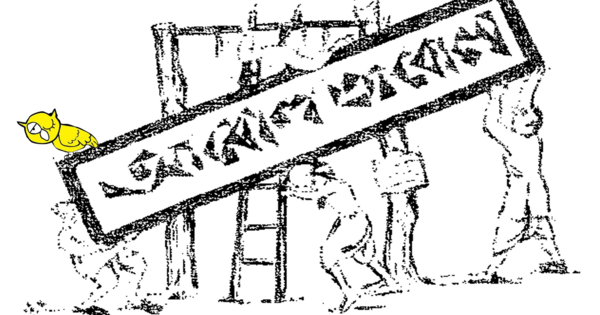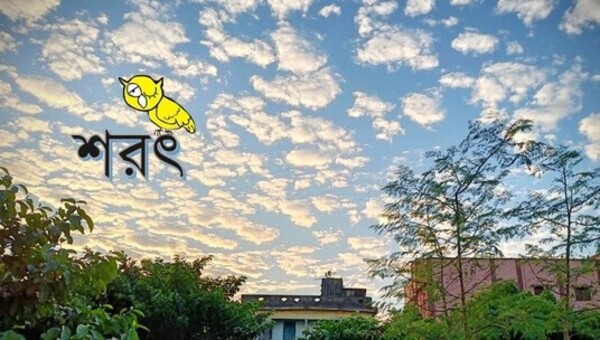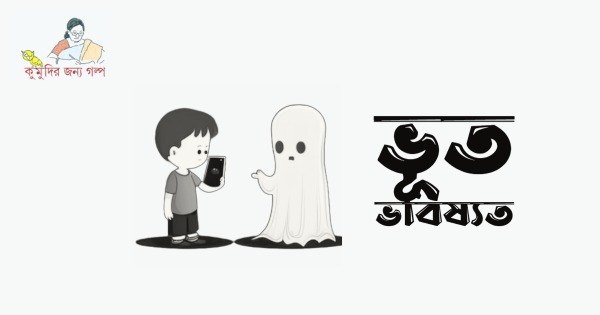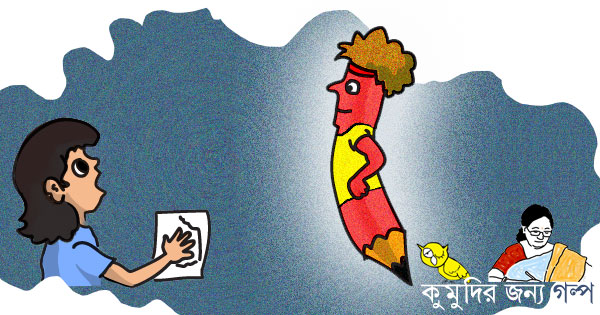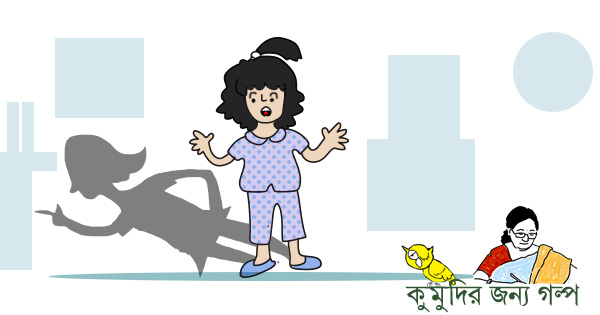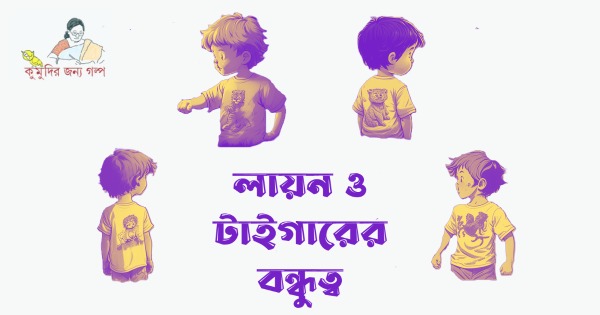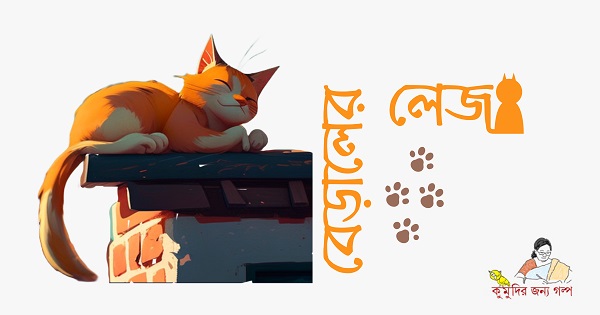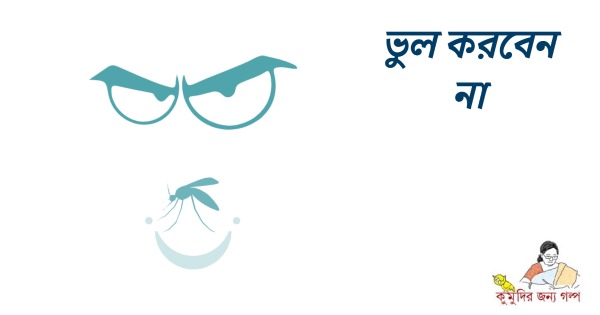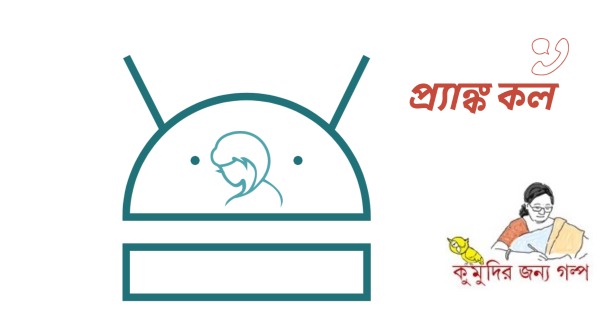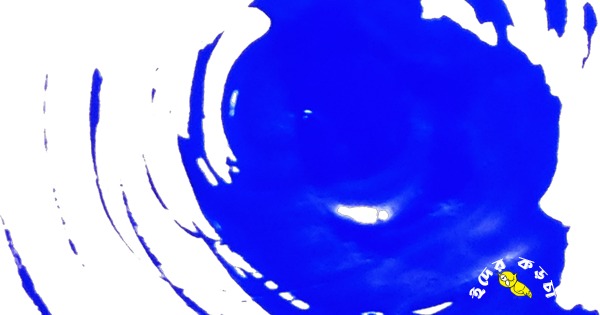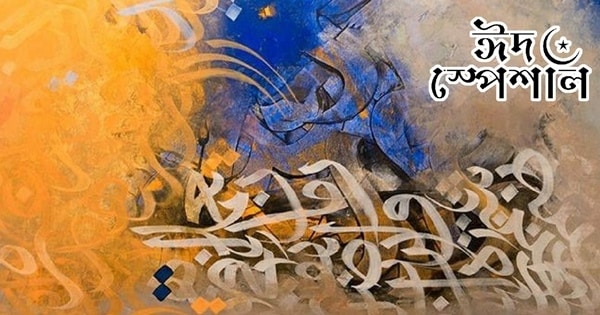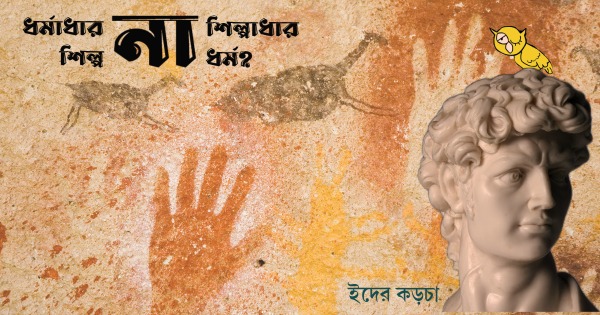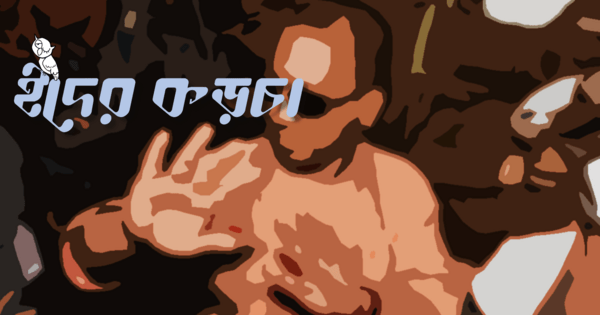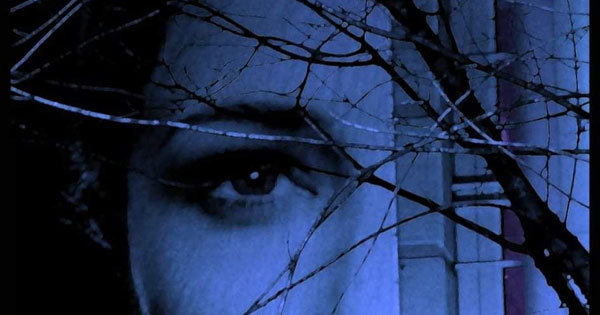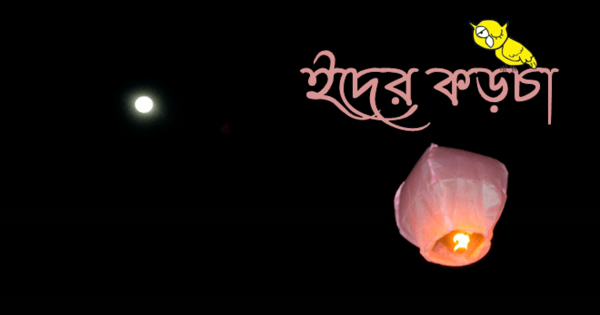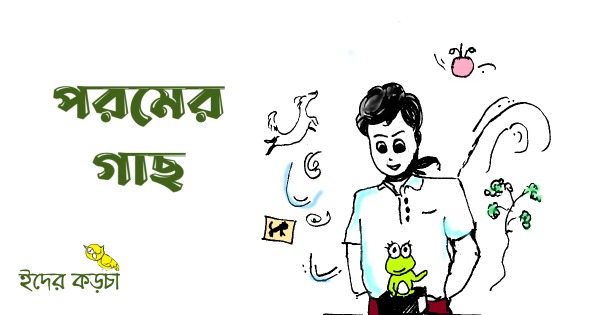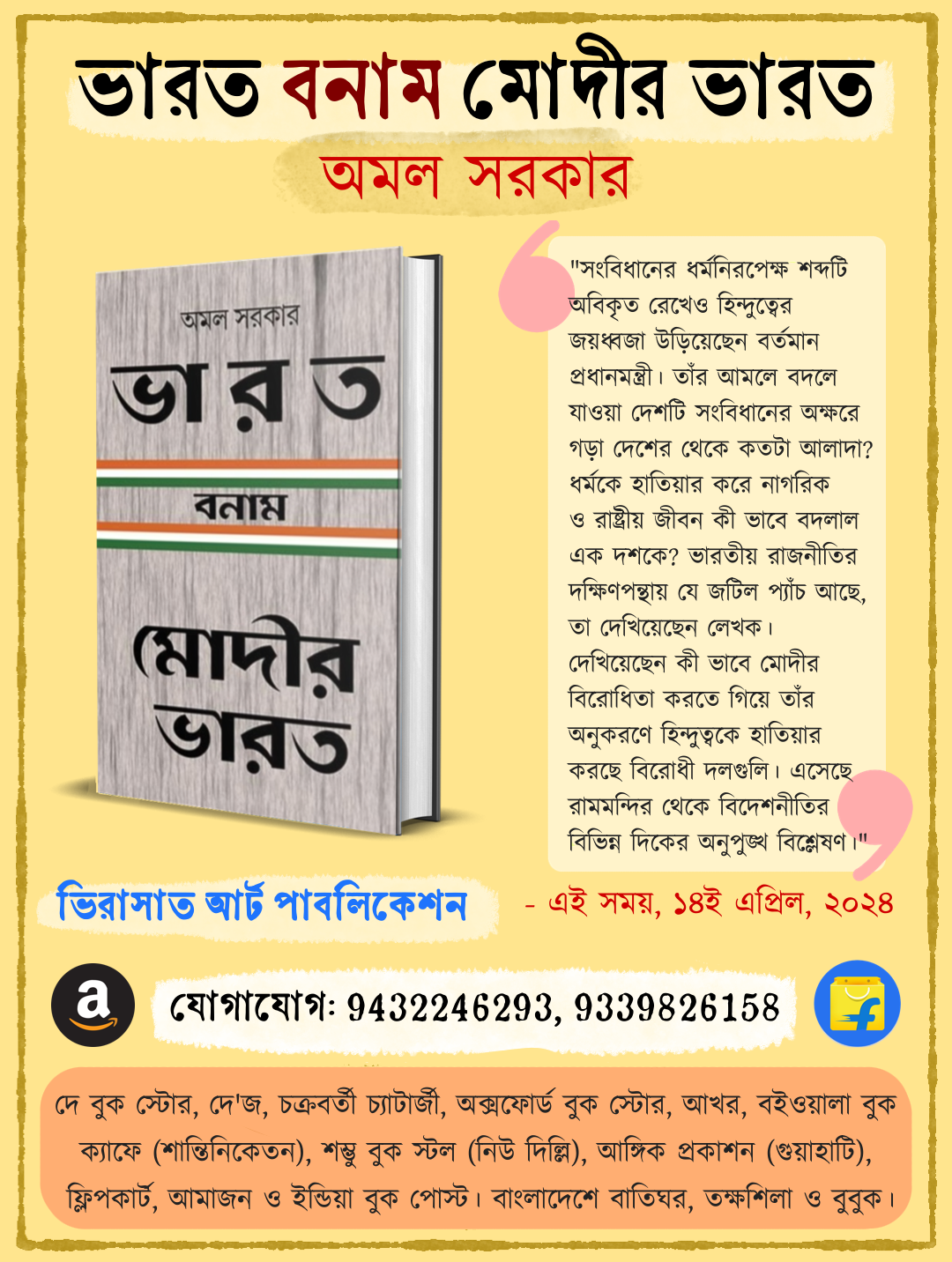তাজা বুলবুলভাজা...
মাইক্রোপ্লাস্টিক ও মানবশরীর - স্বাতী রায় | ছবি: রমিত চট্টোপাধ্যায়‘ঘরের শত্রু বিভীষণ’ মাইক্রোপ্লাস্টিক ২০১৮ সালে ইউরোপ উপকূল থেকে একটি বাচ্চা স্পার্ম তিমিমাছের মৃত্যুর খবরে ‘ইশশ’, ‘আহা’র বন্যা বয়ে যায়। জানা যায় যে তিমি মাছটির পেটে ভরা ছিল বিভিন্ন রকমের প্লাস্টিক ব্যাগ, জালের অংশ, বস্তা এমনকি জেরিক্যানও। বৈজ্ঞানিকদের অনুমান তিমি মাছটি না পেরেছে এই সব প্লাস্টিক শরীর থেকে বার করে দিতে, না পেরেছে সেসব হজম করতে। তার ফলে সম্ভবত পেটের প্রদাহ থেকে গ্যাস্ট্রিক শকে তার মৃত্যু হয়।তবে টিভিতে, কাগজে ছবি দেখে ইসস বলা সহজ, তিমিশাবকটির অবশ্য এত ক্ষমতা নেই যে আমাদের ক্রমবর্ধমান প্লাস্টিক প্রোডাকশনের গ্রাফকে নিচের দিকে টেনে নামায়। তার ছবি দর্শকের মনে যতই আঘাত করুক না কেন! এই তিমিশাবকটি একা নয় কিন্তু, অনুমান যে বছরে প্রায় লাখখানেক তিমি, সীল ইত্যাদি সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী প্রাণী প্লাস্টিকের কারণে মারা যায়, হয় ছেঁড়া জালের টুকরোতে জড়িয়ে ডুবে মরে, আর নাহলে এই বাচ্চা তিমিটির মতন কোন রকম শারীরিক শক পেয়ে। সেই সঙ্গে অনুমান লাখ খানেক সামুদ্রিক পাখি। তারা সমবেত ভাবে মানুষকে কাঠগড়ায় তুলতে পারে না, এই যা বাঁচোয়া। আমরা ডাঙ্গার জীব, সমুদ্রের প্রাণীরা মারা গেলেও যতক্ষণ না আমাদের গায়ে মৃত্যুর ঝাপটা সরাসরি এসে লাগছে, ততক্ষণ আমরা নড়ে বসব কেন? না নড়ে বসতে চাইলে, কেউ অবশ্য জোর করছে না। কিন্তু মুষ্টিমেয় কেউ কেউ হয়ত বুঝবেন যে হয়ত অজানা শত্রু আমাদের দুয়ারেই হাজির। শত্রুর নাম হল প্লাস্টিক। এমনিতে প্রচণ্ড দরকারি জিনিস। কিসে না লাগে! কিন্তু সমস্যা এইটাই যে প্লাস্টিক বলতে আমরা যে বিভিন্ন ধরণের রাসায়নিক দ্রব্য বুঝি, তাদের সবকটিকে পুনর্ব্যবহারযোগ্য করার কোন পকেটসই সুবিধাজনক পরিবেশ বান্ধব উপায় মেলে না। আবার সেটা এমনি ফেলে রাখলে প্রকৃতিতে মিশে যেতে অতি দীর্ঘ সময় লাগে। আর ততদিনে ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে সেটা ম্যাক্রো-প্লাস্টিক মেসো-প্লাস্টিক, মাইক্রো-প্লাস্টিক ইত্যাদি বিভিন্ন আকারের চেহারা নেয়। ম্যাক্রোপ্লাস্টিক হল ২.৫ সেমির থেকেও দৈর্ঘে বা প্রস্থে বড় যে কোন প্লাস্টিকের টুকরো। ৫ মিমি – ২.৫ সেমি অবধি টুকরোকে বলে মেসো-প্লাস্টিক। আর মাইক্রোপ্লাস্টিক বলা হও ১ মাইক্রো মিলিমিটার থেকে ৫ মিলিমিটারের সাইজের প্লাস্টিকের কণা। এই মাইক্রোপ্লাস্টিক নিয়েই আজকের কথা। কারণ আজকের দিনে এরা জলে স্থলে বাতাসে সর্বত্র ভেসে বেড়াচ্ছে। টেকনিক্যালি দেখলে রাসায়নিক দিক থেকে এরা সকলে অবশ্য এক নয়। পলিথিলিন বা পলিপ্রোপাইলিন বা পেট বা পিভিসি ইত্যাদি কোন রকমের প্লাস্টিকের থেকে তৈরি তার উপর নির্ভর করে মাইক্রোপ্লাস্টিকের গোত্র। তবে এক্ষেত্রে গোত্রে কি আসে যায়! কেন মাইক্রোপ্লাস্টিককে বিপদ বলে ভাবছি? এক তো ভারতের অর্থনীতিতে প্লাস্টিক খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ কোটি টাকার মোট ব্যবসা। ২০২৪ থেকে ২০৩০ সালের আনুমানিক বার্ষিক বৃদ্ধি ৬.৬%। প্রচুর লোকের রুজি রোজগার জড়িয়ে আছে এর সঙ্গে। আবার এর মধ্যে মোটামুটি কুড়ি শতাংশের এদিক ওদিক এক্সপোর্ট হয়ে দেশের বিদেশী মুদ্রার ভান্ডার স্ফীত করে। প্লেক্সকনসিল (দ্য প্লাস্টিক এক্সপোর্ট প্রোমোশন কাউন্সিল) সূত্রে পাওয়া যে সরকারি লক্ষ্যই হল ২০২৭ সালের মধ্যে এই বহির্বানিজ্যকে অন্তত আড়াইগুণ বাড়ানো। তাছাড়া নিজেদের জীবনের দিকে তাকালেই বোঝা যায়, প্যাকেজিং থেকে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য থেকে বিলাস সামগ্রীর আবশ্যিক অঙ্গ হিসেবে সবেতেই প্লাস্টিক কিভাবে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে আমাদের জীবনে। সহজে তাকে নিজের জায়গা থেকে নড়ানো যাবে না। কাজেই বোঝাই যাচ্ছে যে প্লাস্টিক, ‘আপনি থাকছেন স্যার’। এদিকে সরকারি হিসেব মতে১, ২০২০-২১ সালেই (পরের বছরগুলির তথ্য মেলেনি) দেশে ৪১ লক্ষ টন প্লাস্টিক বর্জ্য তৈরি হয়েছে। আমাদের পশ্চিমবঙ্গ বছরে ৪.২ টন প্লাস্টিক বর্জ্য উৎপাদন করে ২০২০-২১ সালের সরকারি তথ্য অনুসারে তৃতীয় স্থানে, তেলেঙ্গানা, তামিলনাড়ুর ঠিক পরেই। এই সংখ্যাটাও বছর বছর বাড়ছে। অবশ্যই প্রথম সারির দেশের তুলনায় মাথা পিছু বিচারে কিছুই না এই সংখ্যাটা - আমাদের জনসংখ্যা বিপুল হওয়ায় সুবিধা। তবু সংখ্যাটা তো নিছক অঙ্কের দিক দিয়ে কম নয়। আরও সমস্যা হল আমাদের কথা আর কাজে খুব বেশি সামঞ্জস্য নেই। আর সরকারি হিসেব মতে এই বিপুল পরিমাণ বর্জ্যের দুই তৃতীয়াংশ উৎপাদক কোম্পানির দায়িত্ব। তার পরেও এক তৃতীয়াংশের তো কোন হিসেবই নেই। বাস্তবে কি হয়? তলিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে কোম্পানিরও কিন্তু শুধু প্রসেসিং এর দায়িত্ব, কতটা সত্যি সত্যি কি হচ্ছে তার খবর সব কোম্পানি রাখে কি? এমনিতেও কতটা বর্জ্য কোম্পানি ফিরে পেল, সেগুলো কিভাবে প্রসেস করল, এই ধরণের কোন একাউন্টিং হয় কি? এই বর্জ্য যায় কোথায়? ব্যক্তিগত ব্যবহারের যে প্লাস্টিকের মগ, বালতি, ডাস্টবিন ইত্যাদি কিনি আমরা, সেগুলো কি উৎপাদককে ফেরত দেওয়ার কোন ব্যবস্থা আছে? তার ব্র্যান্ড জিজ্ঞেস করলেই তো বিপদে পড়ে যাব! আর আমরা হেথায় হোথায় যেসব পুরোন প্ল্যাস্টিক ফেলে রাখি, বা সেসব জিনিস জঞ্জালের সঙ্গে ফেলে দিই, তার সামান্য অংশই বাস্তবে রিসাইকল হয়। বেশিটাই রোদে, জলে-বৃষ্টিতে পড়ে থাকে আর ক্ষয় হয়ে হয়ে মাটি-জল-বাতাসে মেশে। মাইক্রোপ্লাস্টিকের সেকেন্ডারি উৎস।অবশ্য এছাড়া ব্যবসার জন্য আলাদা করে মাইক্রোপ্লাস্টিক তৈরি করাও হয়। সেটাই প্রাথমিক উৎস। ওই যে ফাঊন্ডেশনের টিউবটি আপনার ড্রেসিং টেবলে শোভা পাচ্ছে বা যে লিপস্টিক বা ফেস পাউডারটি ছাড়া আপনি বাড়ির বাইরে বেরোতে পারেন না, সেটি কি কি দিয়ে তৈরি আমরা আর কজন জানতে যাই? এই যে বিদেশে অল্পবয়সী মেয়েদের মধ্যে টিউবিং মাস্কারা এত জনপ্রিয়, সেই টিউবটি কিসের তৈরি জানেন কি? “বিট দ্য মাইক্রোবিড” ক্যাম্পেইনের মতে, মেবেলাইন কোম্পানির ৮৫% প্রডাক্টে মাইক্রোবিড ব্যবহার করা হয়। এমনকি আমাদের ঘরের পাশের ল্যাকমে কোম্পানির সানস্ক্রিন লোশন “সান এক্সপার্ট এস পি এফ ৫০ আলট্রা ম্যাট লোশন” এও মাইক্রোবিড মিলেছে। তবে এদেশে যেহেতু এইসব নিয়ে মানুষের মাথা-ব্যথা কম, তাই দেশজ ব্র্যান্ড নিয়ে এখানে মাথাব্যথাও কম। এদিকে বিশ্বজুড়ে কসমেটিকস কোম্পানিগুলোর সর্বমোট বাজার লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে, তাই এখানে মাইক্রোপ্ল্যাস্টিকের বহুল ব্যবহার চিন্তার বিষয় বৈ কি! শুধু একা হরেক কসমেটিকসকে দায়ী করলে হবে না। বস্তুত ২০১৯ সালের নেচারে প্রকাশিত এক পেপারে২ জানানো হয়েছিল যে পরীক্ষা করে দেখা গেছে সাধারণ সিনথেটিক জামাকাপড় বাড়িতে ব্যবহৃত ওয়াশিং মেসিনে কাচা হলে প্রতি কেজি কাপড়ে ১২৮ থেকে ৩০৮ মিলিগ্রাম মাইক্রোফাইবার বেরোয়। অবশ্যই কাপড়ের চরিত্রের উপর নির্ভর করে সংখ্যার এই হেরফের হয়। আর এই মাইক্রোফাইবারের একটা বড় অংশ আবার কোন অধুনা-প্রচলিত বর্জ্য-জল-শোধন প্রক্রিয়ায় আটকানো যায় না। ফলে সেসব সোজা গিয়ে পরিবেশে জমে। এই ডেটার থেকে বিশেষজ্ঞরা অনুমান করছেন যে বছরে যত মাইক্রোপ্লাস্টিক সমুদ্রে গিয়ে পড়ে, তার অন্তত ৩৫% আসে এই কাপড় কাচার থেকে। অবশ্য এই তথ্য মিলেছে ওয়াশিং মেশিনে কাচা কাপড় দিয়ে। এবার কেউ কেউ ভাবতেই পারেন যে ভারত উপমহাদেশে তো এখনও হাতে কাপড় কাচাই বেশি প্রচলিত। তাই বিপদ ওদের, আমাদের আর কি! কিন্তু আসলে সমস্যা আছে। কারণ সমুদ্রের জল আসলে কোন রাজনৈতিক সীমানা মানে না। আর দ্বিতীয়তঃ কাপড়ের থেকে মাইক্রোফাইবার ওঠে মেকানিকাল ও কেমিকাল স্ট্রেসের কারণে। হাতে কাচলে মেকানিকাল স্ট্রেস খানিকটা কম হলেও কেমিক্যাল স্ট্রেসের মাত্রার মনে হয় খুব হেরফের হবে না। আবার ধাই ধপাধপ কাপড় আছড়ে আছড়ে কাচলে কি হয় দেবাঃ ন জানন্তি। এছাড়াও ‘একবার কাচলে কাপড় আবার প্রায় নতুনের মতন হয়ে ওঠে’ এমন ধারার বিজ্ঞাপন দেওয়া বহু ডিটারজেন্ট বা ফেব্রিক সফটনার এর মধ্যেই মাইক্রোপ্ল্যাস্টিক থাকে। ইউরোপের প্রচলিত ব্র্যান্ডগুলোর মধ্যে অন্তত ১১৯ টা ব্র্যান্ডে মাইক্রোপ্লাস্টিক পাওয়া গেছে। সে অবশ্য ইউরোপে বিধিনিষেধও কড়া, ফলে যে সব পদার্থ দিয়ে তৈরি তার সবিস্তার হিসেব প্যাকেটের উপর দিতে হয়। আমাদের অত নিয়মের কড়াকাড়ি নেই। আর ভারতের ব্র্যান্ডগুলো নিয়ে বিশেষ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার হদিশও সহজে মেলে না। অন্য হাতে এক কনজ্যুমার রিপোর্ট৩ বহুল প্রচলিত ১২ টি ডিটারজেন্ট ব্রান্ডের তুলনামূলক পরীক্ষা করে জানিয়েছে যে এদের কোনটাতেই মাইক্রোবিড নেই। কাজেই বৈজ্ঞানিক ভাবে কেউ হাতে কাপড় কাচার পরের বেরোন জলকে পরীক্ষা না করে দেখা অবধি বা ব্র্যান্ডগুলির উপর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষা না হওয়া অবধি আমরা এসব অমূলক ভয় বলে আপাতত নাকে সর্ষের তেল দিয়ে ঘুমাতেই পারি। আমাদের রোজের জীবনে অবশ্য গাড়ীর চাকা ইত্যাদি আরও অনেককিছু জানা-অজানা উৎস থেকেই নিয়ত প্লাস্টিক ক্ষয় হতেই থাকে। তবে স্বস্তির জায়গা খুব একটা হয়তো নেই। এমনিতেই সমুদ্রের ধারে ধারে গবেষণা করে জানা গেছে পৃথিবীর ১৯২ টা উপকূলীয় দেশে যত প্লাস্টিক বছরে তৈরি হয়, তার একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ মাইক্রোপ্লাস্টিক হিসেবে গিয়ে জমা হয় উপকূল অঞ্চলে। আমাদের সুন্দরবন অঞ্চলে প্রচুর প্লাস্টিকজাত দূষণ-পদার্থ সমুদ্রের জলে ভেসে এসে জমা হচ্ছে। আবার ভিতর থেকে যেসব নদী বয়ে যাচ্ছে তারাও প্লাস্টিক দূষক নিয়ে গিয়ে ঢালছে। দুয়ে মিলে সুন্দরবনের অবস্থা করুণ হচ্ছে। আর আমাদের সাধের কলকাতার পাশের গঙ্গার জল নিয়ে পরিবেশবিদদের মাথা ব্যথা অনেকদিনই। সাম্প্রতিক গবেষণায়৪ তাঁরা হুগলি নদীর মিষ্টি জলের এলাকার (অর্থাৎ মোহনার কাছের নোনতা জল বা তারপরের মিশ্র জলের অঞ্চল ছাড়িয়ে আরও উত্তরের অংশ থেকে) থেকে ১০ টি স্যাম্পল নিয়ে তার ভিত্তিতে পরীক্ষা করে জানিয়েছেন যে, সব কটি স্যাম্পলেই মাইক্রোপ্লাস্টিক মিলেছে। সর্বোচ্চ মাত্রায় মাইক্রোপ্লাস্টিক মিলেছে বালিখালের কাছে - ২০৬৯ টি টুকরো প্রতি মিটার কিউব মিষ্টি জলে। এঁদের সংগৃহীত তথ্য সাক্ষ্য দিচ্ছে যে আমাদের আধা পরিশ্রুত বা অপরিশ্রুত বর্জ্য তরলই আসলে মিঠে জলের গঙ্গার জলের মাইক্রোপ্লাস্টিক দূষণের প্রধান উৎস। এছাড়াও অবশ্যই গঙ্গার ধারের বিভিন্ন কলকারখানার থেকে অন্য ধরণের জলদূষণও হয়। কিন্তু সেসব বলতে গেলে নিবন্ধের আকার শুধুই বাড়বে, তাই থাক সে কথা। জলে মাইক্রোপ্লাস্টিকের কথা আগেই আগ্রা, হরিদ্বার, পাটনা এলাহাবাদ এসব জায়গায় নজরে এসেছে। কারোর কারোর মনে থাকতে পারে, কাগজে বেরিয়েছিল, ২০১৯ সালে পলতার জল পরিশোধন কেন্দ্রে মধ্যে ফিলটার করার জায়গায় মাইক্রোপ্লাস্টিক পাওয়া গিয়েছিল।৫ পাওয়া যাওয়ারই কথা। কারণ পলতার জল আসে গঙ্গার থেকে আর গঙ্গার জলই তো দূষিত। আর এটাও বুঝে নিতে কোন অসুবিধা নেই যে এখনও যেহেতু ফিল্টার করে সব মাইক্রপ্লাস্টিক আটকানো যায় না, তাহলে কিছুটা প্লাস্টিক শুদ্ধ জলই আমাদের বাড়ি বাড়ি এসে পৌঁছেছে। আমরা শোধিত জল জেনে সেই জলই পরমানন্দে পান করেছি। কিন্তু হায় এতকিছু জেনেও আমাদের ঘুম ভাঙ্গে না! বিপুল পরিমাণে প্রাত্যহিক বর্জ্য পরিশোধনের কোন মহতী পরিকল্পনাও নজরে এল কি? এই তো আমাদের অবস্থা! অবশ্য জলের কথা বলছি যখন, তখন এই পৃথিবীর হাওয়া, মাটি কিছুই কি আর মাইক্রোপ্লাস্টিক দূষণ থেকে সংরক্ষিত? একেবারেই না। মাইক্রো প্লাস্টিক কণারা সহজেই হাওয়ায় ভেসে ভেসে দূর দূরে চলে যায়। অবশ্য কলকাতার ক্রমনিম্নমুখী হাওয়ার গুণগত মান গোটা পৃথিবীর মানুষের চিন্তার বিষয়। আর তাতে ভাসমান কণারা এতোই বিপজ্জনক মাত্রায় প্রায় সব সময়ই ঘুরে বেড়ায়, তাই সেটাই বড় চিন্তার বিষয়। আলাদা করে মাইক্রোপ্লাস্টিকের উপস্থিতি নিয়ে বিশেষ গবেষণা হয়েছে বলে চোখে পড়েনি। জাপানের বিজ্ঞানীরা অবশ্য শঙ্কা প্রকাশ করেছেন৬ যে বাতাসে ভাসমান কণাদের তো পিএম২.৫ মাপ দিয়ে মাপা হয় আর সেটাকেই স্বাস্থ্যের পক্ষে বিপজ্জনক বলে ভাবা হয়, ভাসমান মাইক্রোপ্লাস্টিক কণারা তার থেকে আকারে বড় বলে হয়ত তেমন নজরদারিতে আসছে না। তাহলে কি স্বাস্থ্যের পক্ষে কী বিপজ্জনক সেটাও নতুন করে ভেবে দেখা দরকার আছে? আর এখন তো (২০২৩ সালের কাগজে বেরিয়েছিল খবরটা৭) হিরোশি ওকোচির নেতৃত্বে জাপানি বৈজ্ঞানিকরা মাউন্ট ফুজির উপর জমে থাকা মেঘের মধ্যেও মাইক্রোপ্লাস্টিকের সন্ধান পেয়েছেন। সমস্যা এই আমাদের পৃথিবীকে ঘিরে রাখা বায়ুমন্ডলে উপস্থিত মাইক্রোপ্লাস্টিক কণারা তারা সমবেত ভাবে মেঘ তৈরি হওয়ার প্রক্রিয়াকেই ঘেঁটে দিতে পারে। সেই সঙ্গে মেঘের থেকে সূর্যালোক প্রতিফলন বা বৃষ্টি হওয়ার ধরণ ইত্যাদি বদলে দিতেও তারা সক্ষম। সব মিলিয়ে পৃথিবীর আবহাওয়াকে বদলে দেওয়ার ক্ষমতা ধরে এই অদৃশ্য কণাগুলো। এমনিতেই আবহাওয়ার বদলের ধাক্কা সামলাতে সামলাতে আমরা নাজেহাল, সেই সঙ্গে আরও বারুদ হয়ত পরিবেশে জমা করছি নিজেদের অজান্তে। আর যে দেশে অধিকাংশ প্লাস্টিক বর্জ্যের ভবিতব্য জমি ভরাট করার কাজে লাগতে সেখানে মাটিও যে প্লাস্টিকময় হয়ে যাবে তাতে আর আশ্চর্য কি? ২০২০ সালেই বর্ধমানের মেমারি অঞ্চলে সমীক্ষা করে গবেষকরা৮ দেখেছেন মাটিতে কিভাবে ম্যাক্রোপ্লাস্টিক ও মাইক্রো প্লাস্টিক দুইই মিশে রয়েছে। তাঁরা এও জানিয়েছেন যে মাটিতে প্লাস্টিকের উপস্থিতি কিভাবে মাটির জলধারণ ক্ষমতা ইত্যাদি চরিত্র বদলে দিচ্ছে। ফলে কৃষি উৎপাদনে প্রভাব পড়ছে। আর সেই প্লাস্টিক গাছের মধ্যে দিয়ে খাদ্যে মিশে মানুষের প্লেটে এসে পৌঁছাচ্ছে। কারণ হিসেবে তাঁরা মূলত দায়ী করেছেন মাটির উর্বরতা বাড়ানোর জন্য দেওয়া আধা-তরল, আধা-কঠিন পরিশোধিত বর্জ্য-অবশেষকে। এতেই প্লাস্টিক ভরা। এছাড়াও আছে প্লাস্টিক আবরণে মোড়া সার (যতদূর পড়েছি, এ বিষয়ে আমার প্রত্যক্ষ ধারনার নিতান্তই অভাব, সারের ধীরে ধীরে মাটিতে মেশা নিশ্চিত করতে প্লাস্টিকের মোড়ক দেওয়া হয়, অন্য কোন কারণ আছে কি?)। এমনিতেই বঙ্গোপসাগরের পাশের সুন্দরবন প্লাস্টিক সেসপিট বলে বহুদিন ধরেই আখ্যা পেয়েছে। সেখানকার মাটি, জল ও প্রাণী-উদ্ভিদের জীবনে মাইক্রোপ্লাস্টিকের প্রভাব নিয়ে অল্প কিছু কাজ তাও চোখে পড়ে। পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জায়গায় এই হিসেব আদৌ হয়েছে কিনা জানা নেই। অথচ বিদেশে বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন যে প্লস্টিক কিভাবে গাছের অঙ্কুরোদ্গমের হারকে বা অঙ্কুরের বাড়কে ব্যাহত করে। মানুষের শরীরে মাইক্রোপ্লাস্টিকের উপস্থিতিরও ক্রমশঃ প্রমাণ মিলছে। নেদারল্যান্ডের ২২ জন প্রাপ্তবয়স্কের মধ্যে ১৭ জনের রক্তে মাইক্রোপ্লাস্টিক মিলেছে। বস্তুত এখনও অবধি পরীক্ষায় আমাদের লালা, রক্তপ্রবাহ, প্লাসেন্টা, কোলন, ফুসফুস, মল ইত্যাদির মধ্যে মাইক্রোপ্লাস্টিক পাওয়া গেছে। মাইক্রোপ্লাস্টিক মিলেছে মাতৃদুগ্ধ ও সদ্যজননীর প্ল্যাসেন্টাতেও। আজকের বিজ্ঞানীরা বলছেন মানুষের শরীরে তিনভাবে মাইক্রোপ্লাস্টিক ঢোকে। প্রথমত শ্বাস গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে ফাইবার বা হাওয়ার সঙ্গে মিশে থাকা কণা হিসেবে এসে শরীরে ঢুকতে পারে। ইন্ডিয়া টুডে গত বছরের একটা খবরে জানিয়েছিল যে আমরা প্রতি সপ্তাহে একটা করে ক্রেডিট কার্ড তৈরি করার মতন যথেষ্ট পরিমাণে মাইক্রো প্লাস্টিক শ্বাসের সঙ্গে টেনে নিই। গবেষণা করে বিজ্ঞানীরা৯ মাইক্রোপ্লাস্টিক কিভাবে মানুষের শ্বাসযন্ত্রের মধ্যে দিয়ে ঘুরে বেড়ায় তার একটা মডেল বানিয়েছেন। নাক দিয়ে ঢুকে শেষে রক্তের সঙ্গে মিশে যায়, তারপর চলতে চলতে সোজা ফুসফুস বা হৃৎপিন্ডে বা অন্যান্য অঙ্গে পৌঁছে যায়। অবশ্য শুধু যে দূষিত হাওয়া দায়ী এমন তো নয়, খাবার বা পানীয়ের মাধ্যমেও মাইক্রোপ্লাস্টিক আমাদের শরীরে ঢুকতে পারে। এই যে গোটা শীতকাল জুড়ে ধাপার কাছের ইস্টার্ণ বাইপাশের ধারে ধারে কলকাত্তাই বাবুদের গাড়ি থামিয়ে নধর সবজি কিনতে দেখা যায়, সেই সব ‘ড্যাঞ্চি’ সবজির সঙ্গে সঙ্গে আমরা কী কী যে খাই কে জানে! তবে এইসব নিয়ে দেশজ রিসার্চ এখনও তেমন মেলে না। তাই আপাতত বিদেশী রিসার্চ থেকেই বলা যাক যে ইটালিতে রোজকার আলু, ব্রকোলি ইত্যাদি সবজির মধ্যেও মাইক্রোপ্লাস্টিক পাওয়া গেছে। এমনকি যে আপেল নিয়ে বলা হয় যে ‘অ্যান অ্যাপেল আ ডে / কিপস দ্য ডক্টর অ্যাওয়ে’, সেই আপেলেও এই দূষকের হদিশ মিলেছে। অবশ্য পরিবেশ-দূষণের আরেকটা ফল হল খাদ্য শৃঙ্খলে মাইক্রো প্লাস্টিকের ঢোকার পাসপোর্ট পাওয়া। ফাইটোপ্ল্যাংটন বা সায়ানোব্যাক্টিরিয়া মারফৎ তাদের খাদক বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে দিয়ে ধাপে ধাপে মানুষের শরীরে এসে ঢোকে। এই যে পাশের বাড়ির দত্তবাবুর বাড়িতে তিনদিন বর্ষার ইলিশ এসে গেল বলে ঈর্ষায় নীল হয়ে গিয়ে আপনি বাজার থেকে বিপুল দাম দিয়ে গোটা ইলিশ কিনে আনলেন আর সোশ্যাল মিডিয়ায় বড় করে ছবি পোস্টালেন, জানেন কি সেই ইলিশের মধ্যে কি কি আছে? অবশ্য বিজ্ঞানীরা বলছেন ত্বকের সংস্পর্শে আসার মাধ্যমেও শরীরে মাইক্রোপ্লাস্টিক লেগে যায়, ভিতরে অনুপ্রবেশ না করতে পারলেও। তার গায়ে লেগে থাকা টক্সিক পদার্থ থেকেও বিপত্তি হওয়া সম্ভব। একবার শরীরে ঢুকতে পারলেই হল, তারপর যে কত রকমের বিপত্তি ঘটাতে পারে! যেমন বেয়াড়া আকারের মাইক্রোপ্লাস্টিকের খোঁচা লাগতে পারে বিভিন্ন অঙ্গ- প্রত্যঙ্গে। প্রদাহ তৈরি হয়। তার উপরে বিভিন্ন মাইক্রোপ্লাস্টিকের রাসায়নিক গড়ন আলাদা আলাদা তো, আর প্লাস্টিক তৈরির পর্বেও বিভিন্ন রাসায়নিক ব্যবহার করা হয়। সবে মিলিয়ে শরীরের ভিতরে বিভিন্ন এন্ডোক্রিন ডিসর্যাপ্টার বা তাদের ক্ষরণে সহায়ক পদার্থ ঢোকে, মোটাদাগের ভাষায়, বহুবিধ হরমোনের গণ্ডগোল সৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়ে। যার ফলশ্রুতি বাড় বৃদ্ধির সমস্যা, বিভিন্ন প্রজনন তন্ত্রের সমস্যা থেকে ক্যান্সার, নিউরোডিজেনেরেটিভ অসুখ অবধি অনেক কিছুই হতে পারে। আরও একটা সমস্যা হল যে মাইক্রোপ্লাস্টিকের গায়ে লেগে লেগে বিভিন্ন হেভি মেটাল বা অন্যান্য টক্সিক পদার্থও শরীরে ঢুকতে পারে, তারাও বিভিন্ন রকমের খেলা দেখায় শরীরে। বলে না একা রামে রক্ষা নেই, সুগ্রীব দোসর! নিরীক্ষায় দেখা গেছে এমনকি কম দূষিত হাওয়াতেও দীর্ঘদিন ধরে শ্বাস গ্রহণের ফলে হৃৎপিণ্ডের বা শ্বাসযন্ত্রের সমস্যা হতেই পারে।১০ খুব সম্প্রতি কালে অবশ্য এক গবেষণায় ২৫৭ জনকে পরীক্ষা করে দেখানো হয়েছে যে যাদের গলার ধমনীতে জমে থাকা প্লাকের প্রলেপের মধ্যে মাইক্রোপ্লাস্টিক মিলেছে তাদের মধ্যে বছর তিনেকের ধারে কাছে হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোক ও তার থেকে মৃত্যুর সম্ভাবনা বেড়ে যাচ্ছে প্রায় সাড়ে চারগুণ। বিপদ বলে বিপদ! এছাড়াও বিজ্ঞানীরা হজমের গোলমাল থেকে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার কমে যাওয়া থেকে অক্সিডেটিভ স্ট্রেস জনিত টিস্যুর ক্ষতি ইত্যাদি বহু শারীরিক বিপদ সম্ভাবনার পিছনেও প্লাস্টিককে চিহ্নিত করেছেন১১ - উৎসাহীরা একটু নেট ঘাঁটলেই বহু তথ্য পাবেন। তবে এই নিয়ে আরও অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা হওয়া প্রয়োজন। যদি বিজ্ঞানীদের বলা এই সব সম্ভাবনা সত্যি হয়, তাহলে মাইক্রোপ্লাস্টিককে নিঃশব্দ ঘাতকের তকমা দেওয়াই যুক্তিযুক্ত হবে। অবশ্য ক্ষয়িত প্লাস্টিকের অপর ফর্ম মানে ন্যানোপ্লাস্টিককেও এই বিপদের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া যাবে না। তবে অবশ্য এই দেড় কোটি মানুষের দেশে মানুষের প্রাণ ম্যাক্রো স্কেলে সব চেয়ে সহজলভ্য। কিছুটা ভারতীয় জীবন দর্শনও হয়ত মানুষকে কিঞ্চিৎ দার্শনিক করে দেয়, তারা ভাবে মরব তো একদিনই, এত না ভেবে আনন্দে বেঁচে নিই। হবে হয়ত। আর যে দেশে এক বিপুল সংখ্যক মানুষ দৃশ্য শত্রুর মোকাবিলা করতে করতেই ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছে সেখানে আর অদৃশ্য শত্রু নিয়ে কেই বা ভাববে! তার উপর এদেশে গবেষণার খাতে যা সামান্য অর্থ ব্যয় হয় আর সম্প্রতিকালে সেই গবেষণা- অর্থের যে ধরণের গবেষণার দিকে গতি, তাতে এই ধরণের অনিশ্চিত গবেষণা তথা প্রকৃত ক্ষতি মাপার জন্য ক্ষেত্র সমীক্ষা কতটা হওয়া সম্ভব সেও বোঝা খুবই সহজ! কাজেই হয়ত না জানা থাকলেই জীবনে শান্তি বাড়ে। আর জেনে গেলে তখন হয়ত ওই বিদেশের মতন নো প্লাস্টিক উইক জাতীয় কিছু নিঃশব্দে পালন করে আত্ম-পাপ ক্ষালনের চেষ্টা করতে হয়। এও জানা যে তাতে সামগ্রিক কোন ছাপই পড়বে না হয়ত। কিভাবে কমানো যায়? ভোগবাদে রাশ টেনে? ব্যক্তিজীবনে বদল এনে? নাকি অন্য কিছু করা দরকার? অবশ্য কি করলে যে সত্যিকারের বদল আনা সম্ভব তাও কি কেউ একা একা বার করতে পারে? ‘একাকী গায়কের’ জন্য কি আদৌ এই গান? সামগ্রিক সর্বস্তরের ঐকান্তিক চেষ্টার দরকার। ব্যক্তি চেষ্টার সঙ্গে সরকারি নীতির সামগ্রিক মেলবন্ধন হলে তবে না কিছুটা কাজ হয়! আর না হলে এই সব লেখা শুধু ভীতি-উদ্রেককারী বলে বাজে কাগজের ঝুড়িতে জমা হয়! ১) https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1943210 ২) De Falco, F., Di Pace, E., Cocca, M. et al. The contribution of washing processes of synthetic clothes to microplastic pollution. Sci Rep 9, 6633 (2019). https://doi.org/10.1038/s41598-019-43023-x৩) https://consumeraffairs.nic.in/sites/default/files/file-uploads/ctocpas/Deterjent_powder.pdf৪) Ghosh, S., Das, R., Bakshi, M. et al. Potentially toxic element and microplastic contamination in the river Hooghly: Implications to better water quality management. J Earth Syst Sci 130, 236 (2021). https://doi.org/10.1007/s12040-021-01733-9৫) https://timesofindia.indiatimes.com/city/kolkata/experts-warn-of-micro-plastics-in-kmc-water/articleshow/69065930.cms৬) Wang, Y., Okochi, H., Tani, Y. et al. Airborne hydrophilic microplastics in cloud water at high altitudes and their role in cloud formation. Environ Chem Lett 21, 3055–3062 (2023). https://doi.org/10.1007/s10311-023-01626-x৭) https://www.thehindu.com/sci-tech/energy-and-environment/japanese-scientists-find-microplastics-are-present-in-clouds/article67356549.ece৮) Maji, Piyush & Mistri, Biswaranjan. (2021). PLASTIC CONTAMINATION, AN EMERGING THREAT FOR AGRICULTURAL SOIL HEALTH: A CASE STUDY IN MEMARI II C. D. BLOCK, PURBA BARDHAMAN, WEST BENGAL, INDIA. Pollution Research. 40. 120-129.৯) Riaz, Hafiz Hamza & Lodhi, Abdul Haseeb & Munir, Adnan & Zhao, Ming & Mumtaz Qadri, Muhammad Nafees & Islam, Saidul & Farooq, Umar. (2024). Breathing in danger: Mapping microplastic migration in the human respiratory system. The Physics of Fluids. 36. 10.1063/5.0205303.১০) Lee Y, Cho J, Sohn J, Kim C. Health Effects of Microplastic Exposures: Current Issues and Perspectives in South Korea. Yonsei Med J. 2023 May;64(5):301-308. doi: 10.3349/ymj.2023.0048. PMID: 37114632; PMCID: PMC10151227.১১) Environ. Health 2023, 1, 4, 249–257 Publication Date:August 10, 2023. https://doi.org/10.1021/envhealth.3c00052ভ্রমণের বিষ - প্রতিভা সরকার | সদা আনন্দময় যে মানুষ হিমাচল প্রদেশে ঢুকলাম শিবরাত্রির সমারোহ মাথায় নিয়ে। জলুসের পর জলুস যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে, সবাই নিজেদের ট্র্যাডিশনাল পোষাকে সজ্জিত, মেয়ে পুরুষের মাথা আচ্ছাদিত, হিমাচলি রঙবেরঙের ঠাটু, টুপি, সব একেবারে জায়গা মত। জিজ্ঞাসা করে জানলাম, সবাই চলেছে মান্ডির তিনশ বছরের পুরানো শিবমন্দিরের দিকে, যে দেবতার এমনই মহিমা, গত বছর জুলাই মাসের বন্যায় আশেপাশে সব রসাতলে গেছে, কিন্তু মন্দিরটির কোনো ক্ষতি হয়নি। পেতলের পাল্কিতে জলুসের ঠিক মাঝখানে দেবতা যাচ্ছেন, তাঁর অঙ্গও পেতলের। নানা রঙের জাব্বাজোব্বা, মস্তকাবরণে তাঁকে প্রায় দেখাই যাচ্ছে না। কিন্তু যে মানুষদের কাঁধে চড়ে তিনি যাচ্ছেন তারা সবাই আনন্দময় গ্রামীণ মানুষ, সাদাসিধে আর বিশ্বাসী।তীর্থান গ্রামের পঞ্চায়েত কার্যালয় প্রাঙ্গণে আর একরকম আনন্দের বিস্ফার দেখলাম দুদিন পর, আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী নারী দিবস উপলক্ষে। পঞ্চায়েত প্রধান মহিলা, সরকারি আধিকারিকও তাই। মাইকে তারা নারী সশক্তিকরণের উদ্দেশে গঠিত বিভিন্ন সেল্ফ হেল্প গ্রুপগুলিকে নানা উন্নয়নমূলক কাজ ও ঋণপ্রকল্প সম্বন্ধে অবহিত করাচ্ছিলেন। তাদের কথা শেষ হতেই মেয়েরা শুরু করল নাচগান। বিভিন্ন গ্রুপের বিভিন্ন ধরণের প্রোগ্রাম। নাম এবং ঠাটুও বিভিন্ন। লক্ষ্মী মহিলা মন্ডলের ঠাটু বা মস্তকাবরণ উজ্জ্বল সোনালী, জাগৃতি নারীশক্তি মন্ডলের বেগুনি, তাতে কুলু স্টাইলের ছাপছোপ। ধর্মীয় নয়, পরম্পরাগত নয়, তবু এই উৎসব গ্রামের বেশিরভাগ মেয়েদের অংশগ্রহণে ধন্য হচ্ছে দেখে ভালো লেগেছে। অনেক কথা হল লক্ষ্মী গ্রুপের প্রধান জি, বিদ্যার সঙ্গে। মেয়েরা এখানে লোনের টাকায় উলের পোশাক বানিয়ে ট্যুরিস্টদের কাছে বিক্রি করে, আচার ঘি জ্যামজেলি ছাড়াও পাইন ফলের অংশ দিয়ে নানা দৃষ্টিনন্দন হস্তশিল্প বানায়। মোটামুটি কিছুটা লাভ থাকে বৈকি বেশির ভাগ গ্রুপেরই। নাহলে হাড়ভাঙা খাটুনির পর মেয়েরা আরও কাজের দায়িত্ব নিতে যাবে কেন! এই জি, বিদ্যার চোখেই সব দেখা হল আমার। পাহাড়ের কোনো দেবতা নেই?তীর্থান গ্রামের মানুষ বিশ্বাস করে, দেবতা মানুষকে এবং জাগতিক সমস্ত কিছুকে রক্ষা করেন সব দুর্ভোগ দুর্বিপাক থেকে। এই বিশ্বাস তীর্থান বা হিমাচলের কেন, হয়ত ভারতবর্ষের সব গ্রামে গ্রামে সব উৎসবের প্রাণ, সব আনন্দের মূল। এই মানুষগুলো শ্রম ও অর্থ দান করে নিজেদের গ্রামের চৌহদ্দিতে মন্দির বানাবে, সেখানে নিত্য পূজার্চনা হবে, তবে না গ্রাম পূর্ণতা পাবে! আমি বিদ্যাকে শুধোই, শুধু পাহাড়ের কি কোনো একক দেবতা নেই, যিনি তাকে রক্ষা করতে পারেন লাগাতার ধ্বংস আর নির্বিচার আক্রমণ থেকে? তাকে বলি, সমস্ত পাহাড়ের রাণী যে হিমাচল প্রদেশ তার চেহারা দিনের দিনের পর দিন যেভাবে কুৎসিত হয়ে উঠছে, তা কল্পনাতীত। পাঞ্জাব পেরিয়ে হিমাচলের সীমানায় ঢুকলেই শুধু উন্নয়ন, নির্মাণ, জেসিপি আর ট্রাকের পর ট্রাক! ট্যুরিজম পয়সা আনে, এজন্য রাস্তার পর রাস্তা তৈরি হচ্ছে, সিঙ্গল লেন ডাবল হচ্ছে বিয়াসের পাশে, সবচেয়ে উঁচু পাহাড়ের মাথায় পৌঁছে যাচ্ছে জেসিপি। ধুলোভরা গাড়ি চলার রাস্তাই হয়ত খুব শিগগিরই উন্নয়নের একমাত্র প্রতীক হয়ে উঠবে। বিদ্যা বা অন্য মেয়েদের বেশি বাইরে যাওয়া হয় না। ক্ষেতি বাড়ি মন্ডলের কাজ সামলাতে অনেক সময় যায়। তবে তারাও শুনেছে পাহাড় ফুটো করা টানেলের পর টানেলের কথা! চল্লিশ কিলোমিটার রাস্তা পেরোতে না পেরোতে পাঁচখানা টানেল ধোঁয়া আর ধুলো ভর্তি বিরাট হাঁ-মুখে মানুষকে গিলে নেয়। টানেল আগেও ছিল, কিন্তু সে সংখ্যায় কম, যাত্রাপথ হ্রস্ব করা ছাড়া তার আর কোনো কাজ ছিল না। এখন তো ভঙ্গুর পাহাড়ের পেট ফুটো করে কেবলই টানেল, জাতীয় নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে। এরকম চললে কোনো যুদ্ধ বাঁধার আগেই পাহাড় ধ্বসে পড়বে, কোনো নির্মাণই বাঁচবে না, সঙ্গে মারা পড়বে অসংখ্য নিরপরাধ মানুষ, ভেঙে পড়বে বাস্তুতন্ত্র। গতবারের সেই বন্যাবিদ্যারা বলে, প্রকৃতির রুদ্ররোষ যে কী ভয়াবহ চেহারা নিতে পারে, তা দেখিয়ে দিয়েছে গতবারের বন্যা। মান্ডির শিবমন্দির বেঁচে গেলেও মানুষের প্রাণ, ঘরবাড়ি, জীবজন্তু, গাছপালা, কিছুই রেহাই পায়নি। বন্যার জল সঙ্গে নিয়ে এসেছে বিশাল ধ্বস, ব্রিজ উপড়ে, জনপদ ভাসিয়ে সে এক প্রলয়ংকর কাণ্ড! মেয়েরা দেখায়, তীর্থান নদীর ওপর এই ব্রিজের নীচে এখনও লেগে আছে এক বিরাট গাড়ির (টাটা হ্যারিয়ার) কংকাল। না বলে দিলে চেনার উপায় নেই। সেতুর মুখোমুখি পাহাড় উপড়ে ধ্বসের সঙ্গে নেমে এসেছে অজস্র ছোট বড় পাথর। ধ্বসের পথে পড়েছিল এক বিরাট গোশালা। দুধেলা গাই সমেত সেটি নিশ্চিহ্ন হয়েছে। জল উঠে এসেছিল অনেকদূর। সেতুটিও বেশ খানিকটা ভেসে গেছে বন্যার জলে। কিন্তু কী আশ্চর্য, নদী সরে আসায় বন্যার পর বোল্ডার পরিকীর্ণ তীর সাফ করে এর মধ্যেই উঠে গেছে হোমস্টে নামের সব ছদ্মবেশী হোটেল। এখন নাকি আইন হয়েছে নদীর গায়ের ওপর নির্মাণ চলবে না। একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। এতদিন এই আইন ছিল না! যেগুলো এরমধ্যেই মাথা তুলেছে সেগুলো আর একটা বন্যায় ধুয়েমুছে সাফ হয়ে যাবে বলে অপেক্ষা থাকবে আমাদের? লক্ষ্মী মন্ডলের লক্ষ্মী মেয়েরাও এই প্রশ্নের সামনে বিমূঢ় হয়ে পড়ে।সব দেখেশুনে মনে হয় ট্যুরিজম একটা ভয়ংকর দৈত্যের চেহারা নিয়েছে। হিমাচল প্রদেশে যেহেতু জমি কেনা যায় না, স্থানীয়দের জমি লিজ নিয়ে হোমস্টে-র নামে হোটেল ব্যবসা খুলে চলেছে রাজ্যের বাইরের ধনী ও প্রভাবশালীরা। স্থানীয়রা লিজের টাকা ও কর্মসংস্থানের অল্প সুযোগই পাওনা বলে মেনে নিয়েছে। কঠিন হাতে এর মোকাবিলা না করলে অচিরেই গোটা হিমালয় ধ্বংস হয়ে যাবে। পরিবেশের সেই নির্বিচার ধ্বংস প্রভাব ফেলবে সারা দেশেই। বিবর্তনের পথে এত সুন্দরের সৃষ্টি হল, সে কি শুধু ধ্বংস হবার জন্যই? তীর্থান গ্রামের মেয়েরা, সমস্ত অধিবাসীরা এ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল এবং চিন্তিতও। কিন্তু এই ধ্বংসযজ্ঞ আটকাবার উপায় তাদের অজানা। বৃহত্তর পরিবেশ ভাবনায় দেশের যে মাথারা ভাবিত হলে কাজ দিত, তারা কোথায়!পরিবেশ ভাবনায় ভারতীয় সংস্কৃতি সাহিত্য: সেকাল-একাল - সন্তোষ সেন | পরিবেশ বিপর্যয় আজ রাষ্ট্রীয় সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্ব চরাচরে পরিব্যাপ্ত। পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বেড়ে ১.৪৪ ডিগ্রির ঘরে, কোন প্রান্তে তীব্র দাবদাহ- খরা-তাপপ্রবাহ; অন্যত্র প্রবল বৃষ্টি-বন্যা-ধস, এমনকি দুটো বিপরীত এক্সট্রিম আবহাওয়া প্রায় একই সময়ে একই স্থানে আছড়ে পড়ছে। হিমবাহের অতিদ্রুত গলন, জল বাতাস নদীর দূষণ জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে প্রবলভাবে। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে সংবিধান-গণতন্ত্র-পরিবেশের সংকট সব জড়াজড়ি করে জট পাকিয়ে তুলেছে। প্রবল মূল্যবৃদ্ধি, বেকারি, আর্থিক বৈষম্য সহ পরিবেশ সংকটের মূল কারণ দেশি-বিদেশি বহুজাতিক কোম্পানির নির্বিচারে জল জঙ্গল জমি পাহাড় নদী: প্রকৃতির সব উত্তরাধিকার লুটেপুটে ধ্বংস করা। পরিবেশ বিঘ্নকারীর সংখ্যা হাতে গোনা হলেও এর প্রভাব পড়ছে নিম্নবিত্ত মানুষ, প্রান্তিক কৃষক, কৃষি শ্রমিক তথা মেহনতি মানুষ ও বনবাসী জনজাতিদের জীবনে। অথচ সমাজের একটা বড় অংশ এখনো কেমন যেন নীরব নিশ্চুপ নিষ্ক্রিয়।এই নিবন্ধের ছোট পরিসরে অতি সংক্ষেপে একটি প্রাথমিক আলোচনা করার চেষ্টা করব ভারতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতি ও মননে পরিবেশ ভাবনার গুরুত্বের ওপর। প্রাণ প্রকৃতি পরিবেশ নিয়ে একটি সুসংহত ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা প্রাচীন ভারতের দর্শনে উপস্থিত ছিল না ঠিকই। কিন্তু অজস্র মনিমুক্তো ছড়িয়ে আছে ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গির অন্তরালে। সিন্ধু সেঁচে এই মনিমুক্তো তুলে এনে আজকের স্থানকালের প্রেক্ষিতে সমাজে প্রথিত করতে পারলে মানব জমিনে নিশ্চিত করেই একটি চারা গাছ রোপণ করা যাবে, যা ডালপালা মেলে শতধারায় বিকশিত হবে। প্রাচীন ভারতের অথর্ব-সংহিতার পৃথিবীসুক্তে ৬৩টি মন্ত্রকবিতা জুড়ে বরফ ঢাকা পাহাড়, ধূলি-পাথর সমাকীর্ণ বিস্তৃত মাঠঘাট, বনজঙ্গল, নদী-সাগর, ছয় ঋতুর সুন্দর সমাহার, নানান কীটপতঙ্গ, পাখপাখালি, ছোট বড় বন্যপ্রাণ: সবকিছু নিয়েই একটা গোটা পৃথিবী ও তার সভ্যতার পরিচয় সুপ্ত আছে। অথর্ববেদের কবির অনুভবে ঔষধি বনস্পতির লালনভূমি বিশ্বম্ভরা বসুধা। নানান জনগোষ্ঠীর বিকাশক্ষেত্রও বটে এই ধরণী। মাটির পৃথিবীর সঙ্গে জীবজগতের এই অন্তরঙ্গতার কথা উঠে এসেছে মহাভারতের কবি ভীষ্মের মুখেও। ভাববাদী দৃষ্টিতে জারিত প্রকৃতি সত্তার অন্তরালে ঋগবেদের সরস্বতী নদী ‘পাবণী জলধারার মূর্তিমতী সুচেতনা’র দেবী হয়ে উঠেছিল। ভূলোক, ব্রহ্মাণ্ড, কিংবা গাছ পাহাড় পাথর হয়ে উঠেছিল দেবতার প্রতীক। তাকে অবলম্বন করে ছান্দোগ্য উপনিষদে সম্পদ-উপাসনার রীতি গড়ে ওঠে। আজও আমরা দেখি আদিবাসী মানুষজন পাহাড় গাছ পাথর নদীকে দেবতাজ্ঞানে (বিমূর্ত ঈশ্বর ভাবনা নয় কিন্তু) পূজা করেন। মনে রাখা দরকার, জঙ্গল পাহাড় গাছ রক্ষার জন্য আদিবাসীদের প্রকৃতিপূজা ও বন জঙ্গলের যৌথ মালিকানার সংস্কৃতি পাহাড় জঙ্গলকে ভয়ংকর ধ্বংসের হাত থেকে একটা মাত্রায় হলেও টিকিয়ে রেখেছে।লতাগুল্ম, ঔষধি-বনস্পতি, জল বাতাসকে সম্বোধন করে তার সাহায্য চাওয়ার কথা এবং গাছগাছড়ার স্বাস্থ্যকর উপকরণের সপ্রশংস উল্লেখ অথর্ববেদে মাঝে মাঝেই উঠে এসেছে। এর মধ্যে আধ্যাত্মদৃষ্টির ভূমিকা স্পষ্ট হলেও বাস্তব উপযোগিতা নির্ধারণের হিসেবি মনোভাবের অসীম মূল্যও কিছু অবজ্ঞা করার নয়।এবার আসি প্রাচীন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি কালিদাসের কথায়। ‘বিক্রমোর্বশীয়’ নাটকে শোকার্ত পুরূরবা হারিয়ে যাওয়া প্রেয়সীর খোঁজে লতাপাতাকে জড়িয়ে ধরেন পরমাত্মীয়ের মতো। মেঘদূতের নির্বাসিত বিরহী যক্ষ মেঘকেই ভাই সম্বোধন করে প্রেমিকাকে দুটো কথা পৌঁছে দেওয়ার জন্য কাকুতি মিনতি করেছিলেন আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে। আর শকুন্তলা নাটকটি কবি রচনা করেছেন প্রকৃতির কথা মাথায় রেখে প্রকৃতির রূপ রস গন্ধের সাথে জৈব-অজৈব প্রাণ ও মানুষের যাপনকে জড়িয়ে নিয়ে। তাই বনবালা শকুন্তলার কাছে বনজ্যোৎস্না লতাটি আদরের ভগিনী হয়ে ওঠে। তার ফুল ফোটার দিনটিকে যৌবন সমাগমের দিন হিসেবে স্মরণীয় করে রাখার জন্য একটি আম্রবৃক্ষের সাথে বিয়ে দেন প্রিয়ংবদা-অনসূয়া সমেত শকুন্তলা। মনমরা হরিণশাবক তাঁদের পালিত সন্তান রূপেই বিবেচিত হয়। শকুন্তলা নিজে সাজসজ্জা পছন্দ করলেও কখনো গাছের জ্যান্ত ফুল ছিঁড়ে খোঁপায় দিতেন না, বরং গাছে ফুল ফুটলে উৎসবের তরঙ্গ বয়ে যেত শকুন্তলার মননে। গাছের গোড়ায় জল না দিয়ে কোনদিন জলপান করতেন না তিনি। অথচ আজ সারা দেশজুড়ে গাছ কাটার ধূম পড়ে গেছে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে। কোন কোন ব্যক্তি/সংস্থার উদ্যোগে কিছু গাছ পোঁতা হলেও তাদের যত্নআত্তির কথা যেন কারোর মাথাতেই আসেনা।পতিগৃহে যাওয়ার দিনে বনের কাঁটাঝোপ, লতাগুল্ম শকুন্তলার কাপড় টেনে ধরে যেন বলে উঠতে চায়, যেও না সখি-আমাদের ছেড়ে যেও না। হরিণীর আর্ত চাহনি শকুন্তলার চোখ ভিজিয়ে দেয়। নিজের মতো সন্তানসম্ভবা হরিণীর নির্বিঘ্ন প্রসবের খবর না পাওয়া পর্যন্ত শকুন্তলার যেন স্বস্তি নেই। কোকিলের কুহূতান না শোনা পর্যন্ত শকুন্তলার পা সরে না। তাঁর কেবলই মনে হয়, অরণ্যদেবী বুঝি যাবার অনুমতি দেননি এখনো। কালিদাসের ভুবনমোহিনী প্রতিভা প্রকৃতির সন্তান শকুন্তলাকে প্রকৃতির সাথে অবিচ্ছেদ্য প্রীতির বাঁধনে বেঁধেছে। উপমা-রূপকের পথ ধরে কুমারসম্ভবেও ফিরে ফিরে আসে প্রকৃতির কথা, প্রাণের কথা, সহজ সরল যাপনের কথা। উপমার ছবি হয়ে ওঠে পুষ্পভর্তি লতার চলাফেরার জীবন্ত চিত্র-বর্ণন। প্রকৃতিকে নিজের অংশ হিসেবে ভাবতে পারতেন বলেই জনৈক বনবাসী রাজা দুষ্যন্তকে হরিণ মারতে নিষেধ করতে পারেন। আরও কিছু অমূল্য সাহিত্য সৃষ্টির দিকে আলোকপাত করা যাক। খেলাচ্ছলে হোক, শিকারের লোভেই হোক ব্যাধের হাতে ক্রোঞ্চবধের নির্মম কাহিনী বাল্মীকির শোকবিহ্বল কণ্ঠে শ্লোক হয়ে ফুটে ওঠে। অন্যদিকে কাদম্বরীতে বানভট্ট একদল মানুষের আত্মঘাতী অরণ্য বিনাশের নিন্দা করেছেন স্পষ্টভাবেই। শালিকলনাথের চোখে একটি গাছ হল ক্লান্ত পথিকের পরম আশ্রয়, যার নিচে বসে মায়ের আঁচলের মতো স্নেহ, স্নিগ্ধ ছায়া পায় পথিকবর। কবি ধর্মপালের মতে তৃণভোজী হরিণের কাছে তৃণভূমি হল মা। আর গাছপালা হল বন্ধু-বান্ধব, নিকট আত্মীয়। ধর্মের ভয় দেখিয়েও প্রকৃতি-মা কে রক্ষার কথা বলেছেন কেউ কেউ। লাঙল চালালে মাটির অনেক পোকামাকড় মারা যায় বলে ব্রাহ্মণের হলকর্ষণ নিষেধ করেছিলেন মনু। তাই বলে ঋষি যজ্ঞব্রত যজ্ঞসভায় পশুবলি দিতে কোনরকম কুণ্ঠা বোধ করেননি।নিসর্গনীতি নিয়ে শাস্ত্রবাক্যের শ্লোক/উপদেশ বা সংস্কৃত সাহিত্য এইভাবে পরিবেশের সাথে মানুষকে সম্পৃক্ত ও অন্তরঙ্গ করে তুলতে চেয়েছে। মাটি আমার মা, গাছ আমার বন্ধু পরমাত্মীয়, জল আমার অন্তরঙ্গ সত্তা, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণুজীব সহ সমগ্র প্রাণীকুল আমার বেঁচে থাকার শর্ত: এই সত্তায় মানুষের মনন জারিত হলে সমস্যার সমাধান অনেকাংশে হয়ে যায়। নিজেকে প্রকৃতির অবিচ্ছেদ অংশ হিসেবে ভাবতে পারলে মুষ্টিমেয় মানুষের দ্বারা পরিবেশে ধ্বংসসাধনের বিরুদ্ধে সে প্রতিবাদের হকদারও হয়ে উঠতে পারে।পরিবেশ ধ্বংস করে আত্মতুষ্টি ও স্বর্গলাভের তীব্র নিন্দা করা হয়েছে পঞ্চতন্ত্রের গল্পে। যেখানে প্রশ্ন তোলা হয়েছে –গাছ কেটে বা পশু হত্যা করে মাটি ভিজিয়ে যদি স্বর্গে যেতে হয়, তবে নরক যাত্রার পথ কোনটা? গাছের ডালে ডালে পাখি, কোটরে পোকামাকড়, ফুলে ফুলে মৌমাছি প্রজাপতিকে আপন করে নিয়ে এক বৃক্ষের দাঁড়িয়ে থাকার কথা সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে পঞ্চতন্ত্রের গল্পে। পুণ্যলাভের পথ হিসেবে দিঘি জলাশয় খনন, সুসংহত বনসৃজনের কথা ধর্মকর্ম হিসেবেই পুরাণে গণ্য হলেও এই বোধটি আজকের দিনে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজনীয়। প্রয়োজন কেবল ধর্মের নামাবলি সরিয়ে নৈসর্গনীতির বোধকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করে যুক্তিবাদী ভিতের ওপর দাঁড় করানো।এই আলোচনায় কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার। অর্থশাস্ত্রের সূনাধ্যক্ষ প্রকরণে হাতি ঘোড়া, কিছু জলচল প্রাণী ও নদী-পুকুর-খাল-সরোবরে জন্মানো মাছ, কোঁচ, জলকাক, হাঁস সহ ময়ূর ময়না ইত্যাদি পাখি সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে। বনে পশুপাখি ধরা পড়লে তাদের জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়ার রাজাদেশও স্থান পেয়েছে অর্থশাস্ত্রে। বেশকিছু মঙ্গলসূচক পশু-পাখি সংরক্ষণের কথাও বলা হয়েছে এখানে। রাজাদেশ লঙ্ঘন করলে শাস্তির বিধান আছে অর্থশাস্ত্রে। যেমন বনে আগুন লাগানোর শাস্তি হিসেবে পুড়িয়ে মারর সুপারিশ করেছেন স্বয়ং কৌটিল্য। জীবন্ত পুড়িয়ে মারার বিধানকে বিরোধিতা করেও বলা চলে, প্রকৃতিসংহার অবশ্যই শাস্তিযোগ্য। এবং এক্ষেত্রে শাস্তির খাঁড়া সুতীক্ষ্ণ করতে হবে পরিবেশ সংহারের মূলহোতা হাঙ্গর কর্পোরেট বাহিনী ও তাদের সেবাদাস নানান কিসিমের সরকার প্রশাসনের দিকেই। অঙ্গুলি হেলন করতে হবে লুটেপুটে খাওয়ার জন্য পরিবেশ আইনগুলোকে পরিবর্তন করার নীল নকশার দিকেও। আসলে পাপপুণ্যের ভয় দেখিয়ে বা নরকবাসের আশঙ্কা জাগিয়ে, কিংবা আচার বিচার ও আত্মশুদ্ধির দোহাই দিয়ে, শাস্তির ব্যবস্থা করে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি বা দর্শন পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে মানুষের ভূমিকা সুনির্দিষ্ট করতে চেয়েছিল। এই বিষয়গুলোই আজকের সমাজ মননে প্রথিত করতে হবে যুক্তিবাদ ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর দাঁড়িয়ে।সেকালের প্রাচীন সাহিত্য: বেদ উপনিষদ এবং প্রাচীন কাব্য ও নাটক, বিশেষ করে সেকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী কালিদাসের সাহিত্য সৃষ্টি একালের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ওপর ভীষণভাবে রেখাপাত করে। কবিগুরুর পরিবেশ ও নৈতিকতা সম্পর্কিত চিন্তাভাবনা সহ তাঁর সমগ্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে একটা কেন্দ্রীভূত মূল সুর রয়েছে। এক অখণ্ড জীবন দর্শনের ওপর ভিত্তি করেই ‘বসুধৈব কুটুম্বকম’ বা সমগ্র বিশ্ব একটি পরিবারভুক্ত, এই বিশ্বমানবতার বোধ গড়ে উঠেছিল রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনে। তিনি মনে করতেন, প্রকৃতি ও মানুষ এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। ‘অরণ্য দেবতা’ প্রবন্ধে কবি বলছেন –মানুষ অমিতাচারী। যত দিন সে অরণ্যবাসী ছিল ততদিন অরণ্যের সঙ্গে তার আদান-প্রদান ছিল। ক্রমে মানুষ যখন নগরবাসী হল, তখন অরণ্যের প্রতি মমত্ববোধও সে হারাল। মানুষ তার প্রথম সুহৃদ তরুলতাকে নির্মমভাবে নির্বিচারে ধ্বংস করে ইটকাঠ আর কংক্রিটের শহর গড়ে তুলতে মনপ্রাণ এক করল। রবীন্দ্রনাথ আরও লিখছেন –অরণ্য ধ্বংস ও বৃক্ষছেদনের ফলস্বরূপ ভারতবর্ষের উত্তর-অংশে গ্রীষ্মের উৎপাত মাত্রাছাড়া হয়েছে। সবুজ বৃক্ষ ও জঙ্গল বিনাশ করে মানুষ যেন দেশে মরুভূমি ফিরিয়ে আনবার উদ্যোগ নিয়েছে। কি অসম্ভব দূরদৃষ্টি। একশত বছর আগে রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে উঠে এসেছে আজকের দিনের ভয়ানক পরিবেশ বিপর্যয়ের স্পষ্ট চালচিত্র। বিপন্ন হিমালয় পৃথিবীর মানচিত্র থেকে উধাও হয়ে গেলে ভারত সহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো রুখাশুখা মরুভূমি বই অন্য কিছু নয়।এই প্রবন্ধেই তিনি লিখছেন –“সেই বিপদ থেকে রক্ষা পেতে হলে আমাদের আহ্বান করতে হবে বরদাত্রী বনলক্ষ্মীকে –আবার তিনি রক্ষা করুন এই ভূমিকে। দিন তাঁর ফল, দিন তাঁর ছায়া।” কবির উপলব্ধি –আধুনিক মানুষ বিলাসবহুল ও প্রদর্শনমূলক জীবনযাপনে নিদারুণভাবে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। বিশ্বমানবতার পূজারী রবীন্দ্রনাথের অন্তর্দৃষ্টি দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্বলোকে পরিব্যাপ্ত। তাই তিনি স্পষ্ট করে বলতে পারেন –“এই সমস্যা আজ শুধু এখানে নয়। মানুষের সর্বগ্রাসী লোভের হাত থেকে অরণ্যসম্পদকে রক্ষা করা সর্বত্রই সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমেরিকাতে বড়ো বড়ো বন ধ্বংস করার ফলে এখন বালু উড়িয়ে আসছে ঝড়, কৃষিশস্যকে নষ্ট করছে, চাপা দিচ্ছে। ….. লোভী মানুষ অরণ্যকে ধ্বংস করে নিজেরই ক্ষতি ডেকে এনেছে। বায়ুকে নির্মল করার ভার যে গাছপালার উপর, যার পত্র ঝরে গিয়ে ভূমিকে উর্বরতা দেয়, তাকেই সে নির্মূল করেছে” (অরণ্য দেবতা)। ‘শান্তিনিকেতন’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখছেন – “যে বিরাট প্রকৃতির দ্বারা মানুষ পরিবেষ্টিত, যার আলোক এসে তার চক্ষুকে সার্থক করেছে, যার উত্তাপ তার প্রাণকে স্পন্দিত করে তুলেছে, যার জল তার অভিষেক, যার অন্নে তার জীবন, …. ভারতবর্ষ সেই প্রকৃতির মধ্যে আপনার ভক্তিবৃত্তিকে সর্বত্র ওতপ্রোত করে প্রসারিত করে রেখে দিয়েছে।” তিনি বলছেন, এই বিশ্বপ্রকৃতির সাথে পবিত্র যোগেই ভারতবর্ষ নিজেকে বৃহৎ করে জেনেছে। আহা, প্রকৃতির সাথে মানবসত্তার কী অপূর্ব আত্মিক যোগ।পাশ্চাত্যের সাথে প্রাচ্য তথা ভারতের প্রকৃতিবোধ ও জীবনদর্শনের স্পষ্ট ফারাক তুলে ধরেছেন তিনি — “শেকসপীয়রের As You Like নাটক একটা বনবাস কাহিনী, টেম্পেস্টও তাই, Midsummer Night's Dream-ও অরণ্যের কাব্য। কিন্তু সে-সকল কাব্যে মানুষের প্রভুত্ব ও প্রবৃত্তির লীলাই একেবারে একান্ত –অরণ্যের সঙ্গে সৌহার্দ্য দেখতে পাইনে। অরণ্যবাসের সঙ্গে মানুষের চিত্তের সামঞ্জস্য সাধন ঘটেনি।”অথচ কালিদাসের শকুন্তলা নাটকের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন তিনি। প্রকৃতিপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘শকুন্তলা’ প্রবন্ধে বলছেন – কালিদাস তাঁর অপরূপ কৌশল ও প্রতিভায় শকুন্তলাকে লীলা ও ধর্মের, স্বভাব ও নিয়মের, নদী ও সমুদ্রের ঠিক মোহনার উপর স্থাপিত করেছেন। তপোবনের প্রকৃতি বর্ণন সম্পর্কে তিনি উচ্ছ্বসিত। তাঁর মতে –তপোবনে স্বভাব এবং তপস্যা, সৌন্দর্য এবং সংযম সব মিলেমিশে একাকার। সেখানে সমাজের কৃত্রিম বিধান না থাকলেও ধর্মের কঠোর নিয়ম বিদ্যমান। শকুন্তলার সহজ সরল সুন্দর অথচ গভীর পবিত্রতা সম্পর্কে তিনি লিখছেন –“শকুন্তলাকেও ধূলা লাগিয়াছিল, কিন্তু তাহা সে নিজেও জানিতে পারে নাই। …. সে অরণ্যের চঞ্চলা মৃগীর মতো, নির্ঝরের জলধারার মতো, মলিনতার সংসর্গেও অনায়াসেই নির্মল।” এখানেই রবীন্দ্রনাথের মহত্ত্ব। তাঁর প্রকৃতিপ্রেম ভীষণ প্রগাঢ় ছিল বলেই ‘ধুলোলাগা মলিন শকুন্তলা’কে তিনি অনাবিল জলধারার সাথে, অরণ্যের সরলা হরিণীর সাথে তুলনা করতে পারেন। নদীর বুকে বড় বাঁধের অযৌক্তিকতা ও বিপদ সম্পর্কে বিজ্ঞানী ও নদী বিশেষজ্ঞরা অনেকদিন ধরেই সরব। ২০২৩ সালে সিকিমে গ্ল্যাসিয়ার লেক আউটবার্স্টের কারণে তিস্তার উপর বড় জলাধার জলের তোড়ে উড়ে যাওয়া এবং কয়েকশ নাগরিকের মৃত্যু নদী বাঁধের বিপদ সম্পর্কে চিন্তাভাবনাকে নতুন করে উস্কে দিয়েছে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ‘মুক্তধারা’ নাটকের কথা আমাদের উল্লেখ করতেই হয়। তিনি প্রকৃতির স্বাভাবিক গতি বা প্রবহমানতা রুদ্ধ করার বিপক্ষে মত ব্যক্ত করেছেন। প্রাকৃতিক জলধারার ওপর আমাদের সকলের সমান অধিকার, তাই এই জলধারার স্রোত বা গতিপথ পরিবর্তন করা অমার্জনীয় অপরাধ। তাই ‘মুক্তধারা’য় শেষ পর্যন্ত এই অপ্রয়োজনীয় বাঁধকে মুক্ত করে স্রোতকে তার নিজস্ব গতিতে বইতে দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হয়েছে।এই নিবন্ধটিকে নির্দিষ্ট অক্ষরসীমার মধ্যে বাঁধতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি ভাবনার আরও নানান পরিচয়: একগুচ্ছ প্রবন্ধ, এমনকি ছোট গল্প বা কবিতার কথা অনুল্লিখিত থাকল। বুঝে নেওয়ার প্রয়োজন পড়েছে যে, আধুনিক ভারতে রবীন্দ্রনাথের হাত ধরে প্রকৃতি ভাবনা, জীবনদর্শন এক উন্নত মাত্রা লাভ করেছে। এই ভাবনা গুলোকে সম্যকভাবে বুঝে নিয়ে আজকের স্থানকালের প্রেক্ষিতে প্রয়োগ করার মধ্য দিয়ে বিশ্বজোড়া প্রকৃতি বিপর্যয়ের সমাধানের তল পাওয়া সম্ভব বলেই মনে করি। বর্তমান যুগের সাহিত্যে, দর্শনে তথা জনমানসে পরিবেশ সংক্রান্ত যে আধুনিক রূপটি ফুটে উঠেছে, তা উল্লেখ করতে হলে সামনে আনতে হবে বর্তমান কালের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন ও তার রূপকারদের। শুধুমাত্র উদাহরণস্বরূপ আমরা উল্লেখ করব চিপকো আন্দোলনের কথা। শ্রদ্ধেয় পরিবেশবিদ সুন্দরলাল বহুগুণা, যিনি হিমালয়কে হাতের তালুর মতো চিনতেন, প্রকৃতিকে ভালোবাসতেন হৃদয় দিয়ে, যাঁর নেতৃত্বে উন্নয়নের অজুহাতে কয়েকশত গাছ কাটার বিরুদ্ধে উত্তরাখণ্ডের আদিবাসী জনগণের বুক দিয়ে গাছ আগলে রাখার আন্দোলন ৫০ বছর ছাড়িয়ে গেল। অথচ উন্নয়নের নামে, নগরায়ণের নামে সবুজ বনানী সহ হেক্টরের পর হেক্টর অরণ্য নিধন হয়েই চলেছে মহা সমারোহে। আজকের দিনের আরেকটি আন্দোলনের কথা সোচ্চারে বলতেই হয়। অবিরল নির্মল গঙ্গার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন জি ডি আগরওয়াল সহ একাধিক সাধুসন্ত। হরিদ্বারের কংখলে মাতৃসদন আশ্রমের সন্ন্যাসীরা জীবনপণ করে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন হিমালয় ও গঙ্গাকে রক্ষা করার স্বার্থে, বিগত দশ বছর ধরে ‘নমোমী গঙ্গা’ প্রকল্পের কোটি কোটি টাকা গঙ্গার জলে তলিয়ে যাওয়ার বিরুদ্ধে, গঙ্গার ভয়ানক দূষণের বিরুদ্ধে। হিমালয়ের কথা এসে পড়লে লাদাখের আদিবাসীদের আন্দোলনের মুখ সোনম ওয়াংচুর কথা স্মরণ করতেই হয়। লাদাখ-কাশ্মীর সংলগ্ন হিমালয় সহ ভারতের বড় বড় নদী, সিন্ধু গঙ্গা অলকানন্দা ধৌলি ইত্যাদি বাঁচানোর লড়াইয়ে আজ প্রচুর মানুষ/সংগঠন এগিয়ে আসছে। এই আন্দোলন গুলিতে প্রাণ সঞ্চার করতে ভারতীয় সাহিত্য, সংস্কৃতি তথা জীবনদর্শনকে সামনে আনতে হবে অনেক বেশি করে, অবশ্যই যুক্তিনিষ্ঠ সত্যের উপর ভিত্তি করেই। ভোগ-সর্বস্বতা সম্পর্কে ‘বিলাসের ফাঁস’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ একটি প্রণিধানযোগ্য বক্তব্য রেখেছেন – “এখনকার দিনে ব্যক্তিগত ভোগের আদর্শ বাড়িয়া উঠিয়াছে। এখন আহার পরিচ্ছদ, বাড়ি গাড়ি জুড়ি, আসবাবপত্র দ্বারা লোকে আপন মহত্ত্ব ঘোষণা করিতেছে। ধনীতে ধনীতে এখন এই লোভের প্রতিযোগিতা। আমাদের দেশে ইহাতে যে কতদূর পর্যন্ত দুঃখ সৃষ্টি করিতেছে, তাহা আলোচনা করিলেই বুঝা যাইবে।”‘আত্মপরিচয়’ গ্রন্থে নবীন রবীন্দ্রনাথের কলমে উঠে এসেছে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের কথা। আত্মপরিচয় এর ভাষা বেশ কাব্যিক মনে হলেও ‘সুদূর বিস্তৃত শ্যামল অঙ্গ’, ‘আমার বৃহৎ সর্বাঙ্গে’, প্রকাণ্ড বৃহৎভাবে এই শব্দগুচ্ছ গুলোর মধ্য দিয়ে তিনি স্পষ্ট করেছেন বিপুলা বিশাল নৈসর্গিক প্রকৃতি তার সমস্ত রূপ -রস-গন্ধ নিয়ে মানুষের বৃহৎ প্রকাণ্ড শরীরকে (এক্সটেন্ডেড বডি) তৈরি করেছে। রক্তমাংসের ক্ষুদ্র শরীরের আরামের মোহে আমরা যতই অন্ধভাবে ছুটি না কেন, সেইটি নেহাতেই আত্মসর্বস্ব এক ক্ষুদ্র ভাবনা। তাই আমাদের আজ ভাবতে হবে অনেক বৃহৎ পরিসরে অনেক বড় পরিধিতে মননকে জারিত করে। ‘আপনা হতে বাইরে দাঁড়া’লে ‘বুকের মাঝে বিশ্বলোকের’ সাড়া মিলতে অসুবিধে কোথায়?ঋণস্বীকার: ১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত – মেঘদূত, কালিদাস, অরণ্য দেবতা, শান্তিনিকেতন, মুক্তধারা, বিলাসের ফাঁস ও আত্মপরিচয়।২। প্রাচীন ভারতের পরিবেশ নীতি: সংস্কৃত শাস্ত্র সাহিত্যের দর্পণে –করুণাসিন্ধু দাশ।
হরিদাস পালেরা...
তোমার বাস কোথা যে...-৫ - Nirmalya Nag | ।। পাঁচ ।। [এই কাহিনীর সব চরিত্র কাল্পনিক। জীবীত বা মৃত কোনো ব্যক্তির সাথে কোনও মিল যদি কেউ খুঁজে পান তা সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত এবং কাকতালীয়। ]অরুণাভর টেস্টগুলো হওয়ার পর কেটেছে দু-তিন দিন। টেস্টের সময়ে বিনীতা হাসপাতালে ছিল, আজ অরুণাভর রিপোর্টগুলো নিয়ে ফেরার কথা। বিনীতার প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছিল হয় সে নিজে যাবে বা বিকাশকে পাঠিয়ে আনিয়ে নেবে। নিজে কাজ ফেলে ২৮-৩০ কিলোমিটার যাতায়াত করবে রিপোর্ট আনার জন্য, সেটা বিনীতার বিশ্বাস হয়নি। যেভাবেই হোক, সেগুলো নিয়ে বাড়ি এলেই ধন্য হয়ে যাবে বিনীতা। আজকাল তার মেজাজ একটু খিটখিটে হয়ে আছে। স্বাভাবিক ছন্দে ফেরার চেষ্টা করছে সে, পারছে না। ডাইনিং টেবিলে বসে সন্ধ্যাবেলায় রঙিনকে পড়ানোর সময়ে বিনীতা বুঝতে পারছিল পড়ানোয় মন নেই তার। রিপোর্টগুলো এলে ফের ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। মেয়েকে অঙ্ক করতে দিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ দেখছিল সে, সেটাও খুব একটা মন দিয়ে নয়। এর মধ্যে গায়ত্রীর ফোন এল।“টেস্টের রিপোর্ট পেলি?” জিজ্ঞাসা করল গায়ত্রী।“এখনও পাইনি, আজ নিয়ে আসবে বলেছে। দেখি আনে কি না,” বলল বিনীতা।“ডাক্তারের সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছিস?”“না, রিপোর্ট আগে হাতে আসুক।”“ঠিক আছে, কাল স্কুলে আসছিস তো?”“মনে তো হয়। অ্যাপয়েন্টমেন্ট তো পেতে হবে ডাক্তারের। কালই পাওয়া যাবে কি না জানি না। পেলে যাব না।”“ঠিক আছে। রিপোর্ট পেলে জানাস,” বলে ফোন কেটে দেয় গায়ত্রী, সহকর্মী হলেও যাকে বিনীতা সব চেয়ে কাছের বন্ধু বলে মনে করে।অঙ্ক করা বন্ধ করে মায়ের ফোনের কথা শুনছিল রঙিন। বিনীতা ফোন কাটার পরে জিজ্ঞাসা করল, “তোমরা কি আবার যাবে ডাক্তারের কাছে?”“হ্যাঁ, বাবার টেস্ট রিপোর্ট পাওয়া যাবে, তারপর।… বিশালের বার্থডের দিন এই ডক্টর আঙ্কলও এসেছিলেন, জানো তো?”“তাই? কী করে জানলে?”“আগের দিন যখন আমরা গেছিলাম সেদিন উনিই বললেন। তোমাকেও দেখেছেন, বললেন সাদা ড্রেস পরেছিলে।”“আমরা বেলুন নিয়ে খেলছিলাম। একটা আঙ্কলের গায়ে বেলুন লাগল, আমায় বেলুনটা দিল, নামও জিজ্ঞেস করল”“উনিই তো,” বলল বিনীতা।“তুমি দেখেছিলে?”মেয়ের সরল প্রশ্নে বিনীতার অস্বস্তি হল, আর অস্বস্তির কারণ বুঝতে পেরে নিজের ওপরেই রাগ হল তার। উত্তর না দিয়ে রঙিনের খাতা টেনে নিয়ে দেখতে লাগল সে। অঙ্কে ভুল দেখে রাগটা গিয়ে পড়ল মেয়ের ওপর।“কী করেছ এটা? টুয়েন্টি-ফাইভ আর থার্টি-ফোর অ্যাড করে ফিফটি-এইট হল কী করে? অ্যাডিশন নতুন করছ না কি? লেখাপড়ায় যদি এতটুকু মন থাকে! ফ্রেশ করে কর।”“পরে করব।”“পরে করব মানে? এখনই করবে। গাদা গাদা ভুল করবে, আর ঠিক করতে বললে পরে করব। কর।”রঙিন মুখ ব্যাজার করে মাথা নিচু করে বসে থাকল হাতে পেনসিল নিয়ে।বিনীতার রাগ কমল না। “কী হল? করছ না কেন?” ধমক দিল মেয়েকে।রঙিন কেঁদে উঠে চলে গেল রান্নাঘরের দিকে। সে জানে বিসার কাছে গেলে আদর পাওয়া যাবে।“রঙিন, রঙিন… এদিকে এস।” ডাকল বিনীতা। মেয়ে এল না। একটু পরে বিসপাতিয়া ভুলিয়ে ভালিয়ে ওকে নিয়ে আসবে। বিনীতার রাগ হতাশায় পরিণত হয়। টেবিলে কনুই আর কপালে হাত রেখে বসে থাকে সে, চোখ অঙ্ক খাতার দিকে থাকলেও দৃষ্টি তার শূন্য। বাইরে গাড়ি এসে থামার হালকা শব্দ শোনা যায়, তার পর কলিং বেল বাজে। বিসপাতিয়া গিয়ে দরজা খুলে দেয়। অরুণাভ ফিরল। ড্রইং রুম থেকে এসে শোবার ঘরের দিকে যাওয়ার পথে ডাইনিং টেবিলের সামনে এসে দাঁড়িয়ে যায় সে।“টেস্টের রিপোর্টগুলো পেয়ে গেছি,” বলল অরুণাভ।বিনীতা যেমন চুপ করে বসে দিল তেমনই থাকে, কেবল মুখটা ঘোরায় স্বামীর দিকে।“কাল যাব ডাক্তারের কাছে। অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছি,” অরুণাভ বলে।অরূণাভ নিজেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছে এটা ভেবে অবাক হয় বিনীতা। তবু হ্যাঁ না কিছুই বলে না সে, মুখ ফিরিয়ে আবার খাতার দিকে চোখ রাখে। ভাবতে থাকে কাল সে কী করবে। অরুণাভর সাথে ডাক্তার ইন্দ্রনীল বিশ্বাসের কাছে যাবে, না কি যাবে না। স্ত্রীর হাবভাব দেখে স্বামীর কী মনে হয় কে জানে। সে বলে, “অত চিন্তা ক’র না, আমার তেমন কিছু হয়নি।”ফোন বেজে ওঠে অরুণাভর। “হ্যাঁ রামাকৃষ্ণানজী, বলুন…,” কথা বলতে বলতে শোবার ঘরের দিকে চলে যায় অরুণাভ। বিনীতা যেমন শূণ্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল, তেমনই থাকে। কী একটা বড় প্রোজেক্ট হাতে নিয়েছে বলছিল, সেটার ভবিষ্যতের কথা ভেবেই কি অরুণাভ নিজেই ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করেছে? গায়ত্রীকে ফোন করার কথা মনে থাকে না তার। আবার মনে হয় কাল অরুণাভর সঙ্গে যাবে কি না। গেলে ডক্টর বিশ্বাস আবার ওকে নিয়ে কিছু বলবেন না তো? কিন্তু আগের দিনও তো তেমন কিছু বলেননি। ফালতু যত ভাবনা মাথার মধ্যে ঢুকে বসে আছে। ডাক্তারবাবু যদি সেদিনের পার্টিতে ওকে বার বার দেখেও থাকেন তাতে কী এসে গেছে? চৌত্রিশ বছর বয়স হয়েছে বলে সে তো আর বুড়ি হয়ে যায়নি। আজকাল তো কত মেয়ের বিয়েই হয় এই বয়সে। সে যাবে, অবশ্যই যাবে কাল অরুণাভর সঙ্গে হাসপাতালে, সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয় বিনীতা। রঙিনের হাত ধরে বিসপাতিয়া আসে। মেয়ে চেয়ারে বসলে বিনীতা নরম গলায় বলে, “অঙ্ক এখন থাক, এস আমরা অন্য কিছু পড়ি। আবোলতাবোল?” প্রিয় বই-এর নাম শুনে মেয়ের চোখমুখ উজ্বল হয়ে ওঠে।“যাও, নিয়ে এস বইটা।”সুকুমার রায়ের ছড়ার বই আনতে মেয়ে নিজের ঘরে যায়। বিসপাতিয়াও ফিরে গেছে রান্না ঘরে। বিনীতা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। ***পরের দিন চেম্বারে বসে সিটি অরুণাভর স্ক্যান রিপোর্ট, এম আর আই রিপোর্ট খুঁটিয়ে দেখছে ইন্দ্রনীল। তার সামনে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই রয়েছে, অরুণাভই আজ ওপিডির শেষ পেশেন্ট। দেখা শেষ হলে পেশাদারী গাম্ভীর্য নিয়ে ইন্দ্রনীল বলল, “টিউমারটা মাঝারি সাইজের। সার্জারি করতে হবে, বায়োপ্সি করে দেখতে হবে ম্যালিগন্যান্ট কি না। তারপর কেমোথেরাপি, তারপর পরিস্থিতি বুঝে অন্য ব্যাবস্থার কথা ভাবা যাবে। সার্জারির ব্যাপারটা দু-তিন দিনের মধ্যে করে ফেলতে পারলে ভাল হয়। সেটা কি পসিবল হবে?”“এত তাড়াতাড়ি?” জিজ্ঞেস করল বিনীতা?“হ্যাঁ ম্যাডাম, অ্যাজ কুইক অ্যাজ পসিবল করে ফেলতে হবে। টাকা পয়সার ব্যাপারটা আপনারা মাধুরীর সঙ্গে কথা বলে জেনে নিন। ইনসিওরেন্স থাকলে সেটার ডিটেলসও জানিয়ে দেবেন। আমি মাধুরীর নম্বর প্রেসক্রিপশনের উল্টোদিকে লিখে দিচ্ছি। রিশেপশন থেকেও জেনে নিতে পারেন কোথায় উনি বসেন।”এতক্ষণে মুখ খুলল অরুণাভ, “অপারেশনের পর ক’দিন ভর্তি থাকতে হবে?”“ধরে নিন পাঁচ-ছয় দিন। তখনকার কন্ডিশনের ওপর ডিপেন্ড করছে।”“তাহলে আমার আর একটু সময় চাই।”“নিন, তবে বেশি নয়। দু-তিন দিনের জায়গায় চার-পাঁচ দিন ম্যাক্সিমাম। প্রতিটা দিনই এখন ইমপরট্যান্ট,” বলল ডাক্তার।প্রেসক্রিপশন লিখে দিল ইন্দ্রনীল, কী কী ওষুধ খেতে হবে জানিয়ে দিল। মন দিয়ে শুনে নিল বিনীতা।“অপারেশন করার ডিসিশন নিলে আমায় ফোন করে জানালেও হবে। আমি মাধুরীকে বলে রাখব। নিজে যদি না আসতে পারেন, কাউকে দিয়ে অ্যাডভান্স টাকা পাঠিয়ে দিলেও হবে। আর হ্যাঁ, ফোনে আমায় না পেলে মেসেজ করে দেবেন, আমি রিং ব্যাক করে নেব।”চেম্বার থেকে বেরিয়ে দু’জনে চুপচাপ হাঁটছিল বাইরের দিকে।বিনীতা বলল, “একটা সেকেন্ড ওপিনিয়ন নিলে হয় না?”“অত সময় নেই। আবার একজন ডাক্তার খোঁজ, অ্যাপয়েন্টমেন্ট কর, সেটা কবে পাব তাও জানি না… একটা বড় প্রোজেক্টে হাত দিয়েছি বললাম না। আমি টাইম চাইলাম সেটার কাজ একটু গুছিয়ে নেব বলে। পাঁচ-ছ দিন আমি অফিস যেতে না পারলে প্রবলেম হবে।”কিছু একটা ভাবছিল বিনীতা। অরুণাভকে বলল বিকাশকে গাড়ি আনতে বলার জন্য। সে চট করে একবার ডাক্তারের কাছ থেকে আসছে।“আবার কী হল? কী জিজ্ঞেস করবে? আমি অফিস যাব তো,” একটু অধৈর্য হল অরুণাভ।“এখুনি আসছি, তুমি এগোও,” বলে দ্রুত ইন্দ্রনীলের চেম্বারের দিকে হাঁটা দিল সে। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল অরুণাভ। তারপর ড্রাইভারকে ফোন করার জন্য মোবাইল বার করল পকেট থেকে।ডাক্তারের চেম্বারের দরজা ঠেলে ঢুকে বিনীতা দেখল ব্যাগ গোছাচ্ছে ইন্দ্রনীল। বিনীতাকে দেখে একটু অবাক হল সে।“কিছু বলবেন, ম্যাডাম?”“আপনি বললেন প্রতিটা দিনই ইমপরট্যান্ট। ওর কন্ডিশন ঠিক কতটা খারাপ?”“আরে না না। শুনুন, এই কন্ডিশন থেকে লোকে সুস্থ হয়েছে এমন অনেক এক্সাম্পল আছে।”“তার মানে কন্ডিশন খারাপ। কতটা? ও কি–”বিনীতার কথা থামিয়ে দিল ইন্দ্রনীল। “শুনুন, যা যা করার সব করা হবে। বললাম না প্রথমে সার্জারি, তারপর–”এবার ইন্দ্রনীলকে থামাল বিনীতা। “ও সব আপনি আগেই বলেছেন। এখন ক্লিয়ারলি বলুন, ও কি টার্মিনাল পেশেন্ট?”“দেখুন ম্যাডাম…”“আমি যথেষ্ট স্ট্রং, আপনি বলুন।”ইন্দ্রনীল চুপ করে থাকে। অরুণাভর গলা পাওয়া যায়, “হাতে আর ক’দিন আছে?”দুজনেই চমকে তাকায়। চেম্বারের দরজায় দাঁড়িয়ে অরুণাভ। তার আসা কেউ খেয়াল করেনি।“অফিসে একটা জরুরী কাজে হাত দিয়েছি, সেটা কমপ্লিট করা দরকার। অন্যান্য ব্যাবস্থাও করতে হবে, তাই সময়টা আমার জানা দরকার।”ইন্দ্রনীল বলল, “সার্জারিটা হয়ে যাক, বায়োপ্সি রিপোর্ট আসুক। তারপর বলব। এখন বাড়ি যান। প্লিজ।”ফেরার পথে গাড়িতে কেউ তেমন কোনও কথা বলল না। অরুণাভ ল্যাপটপ খুলে বসেছিল ঠিকই, তবে বন্ধ করে দিল। বিনীতা জানলা দিয়ে রাস্তার দিকে চেয়েছিল। একবার অরুণাভর দিকে তাকাল, দেখল কোলের ওপর বই নিয়ে বসে আছে সে। তবে পড়ছে না, তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে। (ক্রমশঃ)শিক্ষা নয়, ভিক্ষা - সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায় | কাল থেকে দেখি তথাকথিত বাম-সমর্থকরা ভর্তি করে লিখে চলেছেন, "শিক্ষা নয় জিতল ভিক্ষা"। আশ্চর্য হইনি, কারণ সিপিএমের মিছিলে গুচ্ছের লোক হয়, কিন্তু ভোট পায় বিজেপি। এঁদের সঙ্গে বস্তুত শাইনিং চাড্ডিদের বিশেষ তফাত নেই। রাজনীতি-ফিতি কিচ্ছু না, এঁদের মূলত দুটো দাবী। এক, বাম প্রার্থীরা খুব শিক্ষিত। দুই, পশ্চিমবঙ্গে হাইফাই চাকরি নেই, তাই বেঙ্গালুরুতে (কিংবা টিম্বাকটুতে) গিয়ে করেকম্মে খেতে হয়। শিক্ষিতরা খুব উঁচুদরের লোক, বাদবাকি ফালতু, এটা তাঁদের মাথার মধ্যে গেঁথে আছে, আর শিক্ষিতদের চাই মোটা-মাইনের চাকরি, এইটাকে তাঁরা প্রকৃত কর্মসংস্থান ভাবেন।দুটোই খুব সত্যি হতেই পারে (নাও পারে)। কিন্তু সেটা সমস্যা নয়, সমস্যা হল, এই দুটোই, বামপন্থা ছাড়ুন, যেকোনো মধ্যপন্থী জনপ্রিয় রাজনৈতিক চিন্তারই ঠিক উল্টোদিকে। মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্তদের কর্মসংস্থানের জন্য বিশ্বের প্রায় কোনো জনপ্রিয় নীতিই নির্ধারণ হয়না, হলেও মুখে বলা হয়না। খেটে-খাওয়া-মজদুর ইত্যাদিদের কথা অন্তত কাগজে-কলমে লেখা থাকে, কারণ বুক-বাজিয়ে "আমরা এলিট" বলার মতো দুঃসাহস নেহাৎই আত্মহত্যাপ্রবণ না হলে কোনো রাজনৈতিক দলই দেখায়না। আর শিক্ষিত? নাঃ শিক্ষিতদের পৃথিবীর কোথাও বামপন্থীরা অতিরিক্ত নম্বর দেননা। শিক্ষিতরা ভারতবর্ষে বেশিরভাগই চাড্ডি, সে তো দেখাই যায়। আর পুঁজিবাদীদের স্বর্গোদ্যান আমেরিকাতেও বামপন্থী আইকন খুঁজে বার করতে হলে শ্রমজীবী খুঁজে বার করা হয়। এখন আমেরিকায় যিনি উদীয়মান বাম তারকা, সেই কোর্তেজের শিক্ষাগত যোগ্যতা বিশেষ কেউ জানেনা, কিন্তু তিনি যে অভিবাসী-সন্তান এবং রেস্তোঁরায় কাজ করতেন, জীবনীপঞ্জিতে সগর্বে সেইটাই পাওয়া যায়। খেটে-খাওয়া-মানুষ, এই লাইনটা পছন্দ হোক-না-হোক, ওটা এখনও জলাঞ্জলি দেওয়া যায়নি। যেকোনো গেঁয়ো আনপড় লোককে যদি জিজ্ঞাসা করেন, যে, ভালো নীতি কী, তারা চোখবুজে বলবে, যাতে গরীবের উপকার হয়, সেটাই ভালো। আমাদের বামগরিমায় গর্বিত শহুরে শাইনিংরা এইটুকুও জানেননা, সেটাই প্রমাণ করে শিক্ষা নিয়ে গর্বিত হবার আসলে কোনো মানে নেই, শিক্ষিত হলেই যে ন্যূনতম সাধারণ জ্ঞান থাকবে, তা নাও হতে পারে, বরং গুচ্ছের লোকের দেখা যাচ্ছে সেটা থাকেনা। তা, শিক্ষিত এলিটদের রাজত্ব চাই, এইখান শুরু হয়ে ব্যাপারটা ধীরেসুস্থে অবজ্ঞায় চলে যায়। ভরতুকি মানে ভিক্ষা, বাজে খরচ। বাজারই আসল। তথাকথিত মুক্ত-বাজার একটি আদর্শ জিনিস। বেসরকারি হলেই পরিষেবা 'ভালা হবে'। বাঙালির দ্বারা কিসুই হয়না, কারণ সে ব্যবসা না করে আঁতলামি আর ট্রেড-ইউনিয়ন করে। কিন্তু সিটু? হ্যাঁ, সিপিএম ট্রেড-ইউনিয়ন করত বটে, কিন্তু বুদ্ধবাবুর আমলে ভালো হয়ে যায়, ধর্মঘট চাইতেননা, টাটাকে এনেছিলেন। তারা চলে যাওয়ায় খুব ক্ষতি হয়েছে। ইনফোসিস চলে যাওয়ায় বাঙালির শিরদাঁড়া ভেঙে গেছে, আর টাটা চলে যাওয়ায় মুন্ডুটাই উপড়ে গেছে। - এই প্রজাতির পুরো বক্তব্যই এইটা। মজা হল, এটা শুধু এঁদের বক্তব্য নয়। যেকোনো শাইনিং চাড্ডিকে জিজ্ঞাসা করুন, প্রতিটা পয়েন্টে একদম এক কথা বলবে। দাঁড়ি-কমা শুদ্ধু। বড়জোর এক-আধ জায়গায় নিঃশ্বাস নিতে থামতে পারে। এর উল্টোদিকে কোনো যুক্তি আমি দিচ্ছিনা। শুধু বামপন্থী না, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোপ্রিয় যেকোনো উদারনৈতিক 'শিক্ষিত'র এমনিই জানা উচিত। কেউ কেউ নির্ঘাত জানেনও. কিন্তু তারপরও এরকম অদ্ভুতুড়ে কিছু সমর্থক সব দলেই কিছু থাকে। সেটা দলের সমস্যা না। শিক্ষিতদের প্রার্থী করাতেও সমস্যার কিছু নেই। শিক্ষিত লোকেরা অনেকেই ভালো নেতা, তাছাড়া এরকম তো আইন নেই, যে, বেছে বেছে বস্তি থেকে লোক তুলে আনতে হবে, আর তারাই ভালো নেতা হবে। ফলে ও নিয়ে সমালোচনারও কিছু নেই। কিন্তু সমস্যা হল, এই শাইনিং সমর্থক গুষ্টি, যারা চাড্ডি কিনা বোঝা ভার, সিপিএমের ক্ষেত্রে তাঁরা প্রচুর। অন্তত শহরে। একটা পার্টির সমর্থকরা যে পার্টির ঠিক উল্টো মতে বিশ্বাস করতে পারেন, সেটা এঁদের না দেখলে বোঝা যেতনা। এবং আরও বড় ব্যাপার হল, তাঁরা শুধু সমর্থকদের গণ্ডীতে আটকে নেই। এঁরা শহুরে, বলিয়ে-কইয়ে, প্রভাব-বলয় বিস্তার করতে সক্ষম, এবং এই ল্যাজই ক্রমশ মাথাকে নাড়াতে শুরু করেছে। নইলে, সক্রিয় সমর্থককূলকে এই কথাগুলো বলতে কেউ আটকাতো। অন্তত বিতর্ক-টিতর্ক হত। সেসবের কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছেনা। উল্টে, যেকোনো কারণেই হোক, বাম ঘরানার পুরো আলোচ্যসূচিটাই নির্ধারণ করছেন এই শহুরে শাইনিংরা। এঁরা প্রবল শিক্ষিত, বামপন্থার জ্ঞানে সাক্ষাৎ এঙ্গেলস, শিল্পসংস্কৃতিতে ঠিক যেন দেবী সরস্বতীর বরপুত্র, অভিজ্ঞতায় অতিপ্রাচীন বটগাছ, এবং বাক্যে স্বয়ং ব্যাসদেব। এই শহুরে শাইনিংরাই বামপন্থাকে সংজ্ঞায়িত করছেন, আলোচ্যসূচি তৈরি করছেন, এমনভাবে, যে তাতে স্রেফ লালপতাকা ছাড়া আর বামপন্থা খুঁজে পাওয়া সম্ভব না। এই বিস্তারটা এত গভীরে গেছে, যে, অভিজিৎ গাঙ্গুলির সরাসরি বিজেপিতে ঢুকে পড়তে কোনো অসুবিধে হয়না, এবং ঢুকে পড়ার আগে পর্যন্ত টেরও পাওয়া যায়না, আসলে উনি চাড্ডি। একজন পেশাগতভাবে যে মামলায় উকিল, সেই মামলা নিয়েই তিনি পার্টির নীতিনির্ধারক, এতে কোনো কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট থাকতে পারে, সেটাই কারো মাথায় আসেনা। মিটিং-মিছিলে-ভিডিওয়-রিলে দেখি নাগাড়ে হিন্দি চলছে, পশ্চিমবঙ্গের বেশিরভাগ লোক যে ভাষাটাই বোঝেনা, এটাই মনে হয় কেউ জানেননা। এতে করে পার্টি লাইনের কী সমস্যা হয়েছে, সে আরেকটা বিশদ আলোচনা, এখানে তাতে ঢুকবনা। কিন্তু মোদ্দা কথাটা হল, একটা শহুরে শাইনিং উচ্চ-মধ্যবিত্ত লাইনের আরাধনা চলছে, দেখাই যায়। তাতে পার্টির কী লাভ হয়েছে ঈশ্বর জানেন। কারণ এই লাইনটা বিজেপি আরও ভালো চালায়. আরও স্পষ্ট, আরও সোজাসাপ্টা। সঙ্গে অবশ্য সাম্প্রদায়িকতা গোঁজে। ওইটুকু বাদ দিলে শাইনিং শহুরেপনায় বিজেপি অনেক এগিয়ে। তাই প্রকৃত শাইনিং লোকে খামোখা খোঁড়া বামদের সঙ্গে থেকে কী করবে, সুড়সুড় করে ওদিকেই যায়। সাম্প্রদায়িকতাটা ফাউ। আর যারা শাইনিং নয়, তারাও একাত্ম না হতে পেরে ছিটকে যায়, হয়তো বিজেপিতেই। এই গতিটা, যাকে বামভোটের রামগমন বলা হয়, সে তো এমনি হয়না। গত দশ বছরের কম সময়েই হুহু করে হয়ে গেল এসব। আমরা সব্বাই দেখলাম। আমরা, যারা নেহাৎই দর্শক, কিন্তু বর্গী হানার বিপক্ষে, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পক্ষে, কিঞ্চিৎ বামঘেঁষা, যারা বিজেপি নয় বামদের উত্থান চাই, তারা সাইডলাইনে বসে দেখলাম এবং এখনও দেখে যাচ্ছি, শেষ ট্রেনও ছেড়ে চলে গেছে, তবু নেতাদের আশীর্বাদধন্য কলকাতাইয়া সিপিএম সমর্থকরা "আমরা শিক্ষিত, তোরা ভিখিরি" বলে আওয়াজ তুলছেন, কেউ একটু অন্যকথা বললেই চালচোর বলে দাগাচ্ছেন, "আমরা থাকলে বিজেপিকে অ্যায়সা আটকে দিতাম না" বলে নেহাৎই ফালতু ঢেঁকুর তুলছেন, যেন এখন আটকাতে কেউ বারণ করেছে। সঙ্গে আছে এখানে কাঠি, ওখানে গোষ্ঠী, একে চালচোর বলতে হবে, ও আসলে তৃণমূল। যেন আদতে সেই ২০০৬ এর মতো ২৩৫টা আসনে জিতে ক্ষমতায়, জ্যোতি বসুর জমিদারি ধুইয়েই এখন অনেকদিন চলবে। ওদিকে আসলে কিন্তু সব বাস চলে গেছে, উড়ে গেছে সব পাখি, ভেসে গেছে আঁকড়ে ধরার খড়কুটোগুলি। ফিরে আসা দূরস্থান, বামপন্থাটাই বাদ দিয়ে, বিকাশ-লাইনে চলে, বামরা আদৌ টিকবেন কি? কে জানে।যে যেখানে দাঁড়িয়ে - প্রবুদ্ধ বাগচী | যে যেখানে দাঁড়িয়েপ্রবুদ্ধ বাগচী সাতপাকে বাঁধা লোকসভার নির্বাচন শেষ । এবার ম্যারাপ খোলার পালা ।সেই সঙ্গে মাঠে মাঠে গত দেড় মাসের জমা শুকনো পাতা আর চাপা পড়া ঘাসের আসন্ন বর্ষার অপেক্ষা। অনেক ধুলো উড়ল, অনেক কথা বলা হল, অনেক আশার মেঘ ভেসে বেড়াল নীল আকাশে। আর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই দেশের সব থেকে বড় মেগা-ইভেন্টে ছুটির ঘন্টা বাজবে। পুলিশ, প্রশাসন, নির্বাচনকর্মী, চ্যানেলে চ্যানেলের সাংবাদিক আর অ্যাংকররা একটু নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাবেন। তারপরেই আসবে আবার সরকার তৈরির হিসেবনিকেশ। পৃথিবীর সবথেকে বড় গণতন্ত্রের জন্য এটাও এক বড় মিডিয়া হাইপ। বিশেষত এবারের নির্বাচন অনেকদিন পরে নানা কারণে খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল দেশের ভোটদাতাদের কাছে। একই কথা বলা চলে এই রাজ্যের ক্ষেত্রেও। কিন্তু সব মিলিয়ে কী হবে ? এ নিয়ে প্রচারমাধ্যমে বিবাদ-বিতর্কের কমতি নেই। অমর্ত্য সেন মশাই ভারতীয়দের যুক্তিশীল বা আর্গুমেন্টেটিভ হওয়ার কথা বলেছিলেন। তাঁর সেই প্রত্যাশা কতদূর মিটেছে জানা নেই তবে টিভি চ্যানেলে হরেক রাজনৈতিক যুক্তিতর্কের ‘মিডিয়া শো’ আজকাল সকলে ভাল খায় যার দরুন ওই প্রাইম-টাইমে বিজ্ঞাপনী আয় প্রচুর। আমরা আমাদের আলোচনা সীমিত রাখছি শুধু এই রাজ্যের কয়েকটি সম্ভাব্যতার ওপর। নানান মাধ্যম থেকে সংবাদ সংগ্রহ করে ও নানা ধরনের প্রচার বিশ্লেষণ দেখে সাদা চোখে কয়েকটা কথা আমার মনে হয়েছে। এই রাজ্যে এবারের লোকসভা নির্বাচনের প্রচারের ধরন ছিল খুব ঘোলাটে। বিগত বিধানসভায় রাজ্যে বাম ও কংগ্রেস দলের শোচনীয় পরাজয় ও আসন সংখ্যার নিরিখে শূন্যে নেমে যাওয়ায় সাধারণভাবে মনে হয়েছিল টি এম সি ও বিজেপি যেন কিছুটা অ্যাডভান্টেজ নিয়েই খেলা শুরু করবে। কিন্তু ২০২১ সালের পরাজয়ের পর থেকে সি পি এম এর নেতৃত্বে বাম ব্রিগেড কিন্তু আস্তে আস্তে সাংগঠনিক শক্তিকে মেরামত করতে করতে এগিয়েছে। রাজ্য সম্পাদক হিসেবে মহম্মদ সেলিমের সামনে থেকে নেতৃত্ব দেওয়ার প্রবণতা বসে যাওয়া কর্মীদের জন্যও ছিল স্টিমুল্যান্ট। আর বিগত বিধানসভার পরে পরেই রাজ্যের একের পর এক বিপুল দুর্নীতির ‘ভান্ডাফোড়’ টিএমসিকে খুব মসৃণভাবে পা ফেলতে দেয়নি। শিক্ষা নিয়ে চাকরি নিয়ে খাদ্যশস্য নিয়ে ঘোর দুর্নীতিতে বাংলার মন্ত্রী উপাচার্য শিক্ষা দফতরের মাথারা একসাথে জেলে ঢুকেছেন —- স্বাধীনতার পরে বাংলায় এই উদাহরণ নেই। এবং নানা মিডিয়ার চর্চায় এটাও ইঙ্গিত মিলেছে আরো উঁচুতলার প্রশাসন এর সঙ্গে যুক্ত, নানা প্রতিবন্ধকতায় তাঁদের নাগাল পাওয়া যাচ্ছে না। তথ্যপ্রমাণ কি কতটা আছে কেউ জানেন না কিন্তু পাবলিক পারসেপশন বলে একটা বিষয় আছে, তাতে টিএমসি সুপ্রিমো থেকে তাঁর সেকেন্ড-ইন-কম্যান্ড সবাই একটা অদৃশ্য জিজ্ঞাসাচিহ্নের সামনে আছেন। আর কেন্দ্রীয় শাসক দলের সঙ্গে বাড়তি সখ্যের সূত্রে যে কেন্দ্রীয় এজেন্সির তদন্ত রাজ্যে ক্রমশ ধার হারিয়ে ফেলছে এটাও আর অস্বীকার করার জায়গায় নেই, হাইকোর্টের বিচারপতি অবধি প্রকাশ্যে একথা বলে ফেলেছেন। সারদা কান্ডের তদন্তের জন্য লোকসভার এথিক্স কমিটির অনুমোদন আজ প্রায় দশ বছরেও এসে পৌঁছায়নি, ওই কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন লালকৃষ্ণ আদবানি। প্রশ্ন উঠবে না ? শিক্ষায় নিয়োগ দুর্নীতি ও কয়লা বালি পাচারে অভিযুক্ত যুব তৃণমূল নেতা বিনয় মিশ্র চোখ এড়িয়ে বিদেশে গিয়ে ঘাঁটি গেড়েছেন, এটা কি কেন্দ্রের অভিবাসন দফতরের সঙ্গে যোগসাজশ ছাড়া সম্ভব ? যেখানে কিছু কিছু অভিযুক্ত ‘প্রভাবশালী’ এই পরিচয়ে জেলে বন্দি সেখানে কয়লা পাচার কান্ডের আরেক অভিযুক্ত অনুপ মাজি (লালা) কীভাবে একদিনের মধ্যে জামিন পেয়ে গেলে এর কৈফিয়ত কেন্দ্রীয় তদন্তকারী এজেন্সি দেবেন না ? এইসব পূর্বাপর বিবেচনা করে টিএমসির এই ভোটের প্রচার ছিল একেবারেই অন্যরকম ও মূলত অপ্রাসঙ্গিক। নিজেদের সরকারের অনুদান-নীতিকে তারা সামনে এনেছেন প্রচারে —-- লোকসভা ভোটের সঙ্গে যার কোনো যোগই নেই। দেওয়ালে ‘লক্ষ্মীর ভান্ডার’ এর ছবি এঁকে বা কন্যাশ্রীর কথা আউড়ে দিল্লির ভোটে কী হবে কেউই বুঝতে পারেননি। লোকসভায় যিনিই জিতুন রাজ্য সরকারের ঘোষিত প্রকল্প বন্ধ বা চালু করার তাঁর কোনও ভূমিকা থাকে না। ভোটের বাজারে এই সত্যি না বলে তারা কি একরকম ভয় দেখিয়ে রাখলেন মানুষকে? সভায় সভায় তাঁরা প্রকাশ্যেই বলেছেন, অন্য কেউ জিতলে সমস্ত অনুদান বন্ধ হয়ে যাবে। এখানে অবশ্য বিজেপির প্রধান সেনাপতি শুভেন্দুর একটা কথা খেয়াল করতে হবে। তিনি বারবার বলেছেন বিজেপি রাজ্যে কুড়িটার বেশি আসন পেলে এখনকার সরকারকে ফেলে দেওয়া হবে। এর আগেও তিনি এরকম দিন তারিখ বার ঘোষণা করে জন মানসে ‘খেলো’ প্রতিপন্ন হয়েছেন আর এই ধরনের মন্তব্য সুস্থ গণতান্ত্রিক চেতনার প্রকাশ নয়। বরং এই জুজু দেখিয়ে টিএমসি তাঁদের হরেকরকম ‘শ্রী’ আটকে দেওয়া হবে এমন এক বিকল্প প্রচারের অক্সিজেন পেয়ে যায়। গেছেও। একেকটা সভায় টিএমসি বক্তাদের কথা শুনে মনে হয়েছে তারা যেন পাড়ার পুরসভার ভোটের প্রচার করতে এসেছেন। একইভাবে বিজেপি তাঁদের সেরা সেরা প্রচারক নিয়ে এসেও খুব আস্থা জাগানোর মতো কিছু বলেননি। তাঁদের খুব পছন্দের ‘ইয়র্কার’ ছিল ধর্মীয় মেরুকরণ —- তবু রাম মন্দিরের মেগা ইভেন্ট যেভাবে প্রচারের পাল টেনে নিয়ে যাবে বলে তারা মনে করেছিলেন তা হয়নি। এই রাজ্য শুধু নয় কর্ণাটক, অন্ধ্র, বিহার, মহারাষ্ট্রের সাধারণ তরুণ-যুবাদের বলতে শুনেছি কাজ না পাওয়ার কথা, তারা তাঁদের ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন টিভির ক্যামেরায়। অথচ দেশজোড়া বেরোজগারির প্রশ্নটা বিজেপির ভাষ্যে প্রায় উপেক্ষিত। বরং ২০১৪-তে বছরে দুকোটি চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি যে আদপে ছিল বেকারদের জন্য ধাপ্পাবাজি এটা সবাই ধরে ফেলেছেন। দশ বছর সরকার চালানোর পর কার্যত বিজেপির সামনে কোনো ইস্যুই ছিল না। তাই শেষদিকে প্রধানমন্ত্রী ধ্যানে বসার আগে অবধি মঙ্গলসূত্র কেড়ে নেওয়া, মোগলাই খানা, দেশের সম্পদ কেড়ে মুসলিমদের দেওয়া হবে এইসব নির্লজ্জ মিথ্যে প্রচার করে নিজেকে টেনে নিচে নামিয়েছেন। দেশের কোনও প্রধানমন্ত্রীর মুখে এত অসত্য এত অবান্তর এত কুৎসিত কথা আমরা ইতিপূর্বে শুনিনি। বিপরীতপক্ষে নিজেকে অবতার বলে প্রচার করে মানুষের সেন্টিমেন্টে সুড়সুড়ি দেওয়া বা ২০৪৭ সালের উন্নত ভারতের ‘আজগুবি স্বপ্ন’ ফেরি করা —এর সবগুলোই ছিল ‘নেই কাজ তো খই ভাজ’ ধরনের। মাঝে মধ্যে এসে অবশ্য বিজেপি এই রাজ্যের নানা দুর্নীতির কথা তুলেছেন এবং তাঁর প্রতিবিধানের কথা বলেছেন। কিন্তু এর সারসত্য নিয়েও তো ঘোর সংশয়। রাজ্যের শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির সঙ্গে খোদ শুভেন্দুর নাম জড়িয়ে আছে, সারদা নারদায় তিনি আপাত অভিযুক্ত —- আছে আরো কিছু চুনোপুটির নাম যারা এখন বিজেপির ঘরে। যে ভাইপো-র দুর্নীতি নিয়ে তারা এত সরব তাঁর ‘কুকীর্তির’ জরুরি সাক্ষী কালিঘাটের কাকুর কণ্ঠস্বর আজও তদন্তের সহায় হতে পারল না, শোনা যাচ্ছে পিসির সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সাক্ষাতের পরেই নাকি কয়লাপাচারের চার্জশিট থেকে ভাইপোর নাম বাদ পড়েছে। আরও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা দেখা গেল, ভাইপোর ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রটিতে জোরালো লড়াই দেওয়ার বদলে কার্যত দুর্বল প্রার্থী দিয়ে এবং তারকা প্রচারকদের তাঁর ধারেকাছে না নিয়ে গিয়ে বিজেপি তাঁকে একরকম ওয়াকওভার-ই দিয়ে দিল। আর দুর্নীতির বৃহত্তর ক্ষেত্রে তো বিজেপি চ্যাম্পিয়ন। ইলেক্টরাল বন্ড কান্ডে, পি এম কেয়ার্স ফান্ডে তাঁদের তোলাবাজির ছাপ স্পষ্ট। সেইসঙ্গে বিভিন্ন রাজ্যে কোনো-না-কোনো আর্থিক দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত নেতাদের সাদরে নিজেদের দলে ঠাই দিয়ে তারা তো ওয়াশিং মেশিন অভিধাই পেয়ে গেছেন! বিজেপি আর টিএমসির এই বাইনারির ভিতরে দাঁড়িয়ে এবারেই রাজ্যের বাম-কংগ্রেস জোট একটা নতুন ভাষ্য লোকসভার ভোটে নিয়ে এসেছেন। বিজেপি আর টিএমসি যে আসলে নিজেদের মধ্যে গোপন সখ্য রেখে চলে এই কথাটা এর আগেও তারা বলার চেষ্টা করেছেন — কিন্তু প্রচারটা তেমন দানা বাঁধেনি। কিন্তু গত তিন বছরের রাজ্য-রাজনীতি সেই ‘গোপন সেটিং’-কে কার্যত প্রামাণ্য করে তুলেছে। আসানসোলের দাঙ্গায় অভিযুক্ত, যাদবপুরের ছাত্রনিগ্রহে যুক্ত বাবুল সুপ্রিয়-র টিএমসিতে ফেরা ও এক ধাক্কায় মন্ত্রিত্ব পাওয়া আমাদের কাছে ভাল বার্তা দেয়নি। এর পরে শুরু হয় বিধানসভায় বিজেপির হয়ে জেতা বিধায়কদের পদত্যাগ না-করে টিএমসিতে ফিরে আসা। এঁদের সর্দার মুকুল রায় ইদানিং বলছেন যা বিজেপি তাই তৃণমূল ! সত্যিই তো এই লোকসভার প্রার্থী নির্বাচনে আমরা দেখলাম টিএমসির অনেকগুলি প্রার্থী ‘দলবদলু’ বিজেপি হিসেবে টিকিট পেয়ে গেলেন আর একইভাবে টিএমসি-র শিবির বদল করে তারা বিজেপির ঘরেও সানন্দে ও সসম্মানে ভিড়ে গেলেন। ১০মার্চ ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডের সভায় অর্জুন সিং তাঁর বাহিনী নিয়ে টিএমসির সভায় এসেছিলেন, সভা থেকে যখন তাঁর নাম ব্যারাকপুরের প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করা হল না — ফেরার পথে তিনি ভাটপাড়ায় তাঁর দলীয় অফিসে দিদির ছবি নামিয়ে মোদির ছবি টাঙিয়ে দিলেন এবং মোদির দল তাঁকে প্রার্থীপদও দিয়ে দিল —-কী অবাধ আর অনায়াস চলাচল ! যে একশো দিনের কাজ বা আবাস দুর্নীতি নিয়ে ভাজপা সরব, যেখানে তাঁদের হাতে পঞ্চায়েত ছিল তারাও একইভাবে অর্থ তছরুপ করেছেন। উদাহরণ বাড়িয়ে যাওয়া সম্ভব। এই জায়গায় এবারের বাম কংগ্রেস জোট অনেকটা জোরের সঙ্গে ইস্যুগুলো সামনে এনেছেন, পর্দা ফাঁস করেছেন এই গোপন দাম্পত্যের —-- মানুষও নিজের অভিজ্ঞতায় বুঝেছেন এই সখ্য। পরিবর্তে অনেকদিন বাদে বাম প্রার্থীরা কিছু মৌলিক দাবির কথা তুলেছেন যা নির্বাচনের ফাঁকা দামামায় ঢাকা পড়ে যাচ্ছিল। বিশেষ করে কাজের অধিকারের দাবি, চুক্তি চাকরির বদলে স্থায়ী চাকরির দাবি, শিক্ষাকে কলেজস্তর অবধি অবৈতনিক করার দাবি, স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে আরো বেশি উন্নত করার দাবি ইত্যাদি ইত্যাদি। পাশে পাশে শিল্প স্থাপনে রাষ্ট্রীয় পুঁজির বেশি অংশগ্রহণ, পরিবেশবান্ধব শিল্পের প্রসার এগুলির কথাও বলা হয়েছে। এর প্রতিটিই সংগত এবং দেশজোড়া কর্মসংস্থানের অভাবের প্রেক্ষিতে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। বামেদের তরুণ ও প্রবীণ প্রার্থীরা উদয়াস্ত খেটে এগুলোকে মানুষের কাছে তুলে ধরেছেন যা নিশ্চয়ই প্রশংসার দাবি রাখে। যে ফ্যাসিবাদের উত্থানের আশঙ্কার কথা আজ বলা হচ্ছে, ঐতিহাসিকভাবে তার জন্য দরকার হয় এক পোক্ত বেকার বাহিনী, সেই বাহিনীর ভিত্তি ক্রমশ পাকা হচ্ছে। অনেকেই হয়তো জানেন, ২০১৯ সালে বিজেপি কেন্দ্রীয় সরকারে আসার পরে ‘নমো ব্রিগেড’ নামক একটি সংস্থা স্বল্প বেতনে অনেক কর্মী নিয়োগ করেছেন শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রীর প্রচারের জন্য। কাজেই বামপন্থীরা যে ‘রুটি রুজি হকে’র কথা বলে এবার প্রচারের অভিমুখকে কিছু অপ্রাসঙ্গিক খেউড় থেকে বার করে আনার চেষ্টা করলেন তা একটি বলার মতো কথা। খুব সংগত কারণেই বামপন্থীরা এবারে মানুষের সমর্থন প্রত্যাশা করেন। কিন্তু সম্ভাব্যতা কয়েকটি। বিজেপি যদি পুনরায় ক্ষমতায় ফেরে এবং বামপন্থীরা যদি নিজেদের ক্ষমতা কিছুটা বাড়িয়ে নিতে পারে তাতে সংসদের ভিতর তাঁদের সোচ্চার কন্ঠ আমরা নিশ্চয়ই শুনব। কিন্তু তাতে চিড়ে ভিজবে না। কারণ, তৃতীয়বার ক্ষমতায় ফিরলে বিজেপি আর্থিক সংস্কারের ক্ষেত্রে আরও জোরাল রোড রোলার চালাবে এটা সুনিশ্চিত। শিক্ষা স্বাস্থ্যসহ অত্যাবশকীয় ক্ষেত্রগুলিতে আরও আরও বেসরকারি বিনিয়োগকে প্রোমোট করে তাঁরা মানুষের ওপর বোঝা চাপাতে কসুর করবে না। আর সংসদে বিরোধী কন্ঠকে এখনই তাঁরা গুরুত্বহীন বলে মনে করে, এই মনোভাব রাতারাতি পাল্টে যাবে এমন নয়। ফলে নির্বাচকমণ্ডলীকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি আদপে রূপায়ন করা অসাধ্য। আর যদি ইন্ডিয়া জোট সরকার গড়ার মতো অবস্থায় আসেন এবং বামপন্থীদের সমর্থন খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে তাহলে বাম সাংসদরা কিছুটা সুবিধেজনক অবস্থায় থেকে নিজেদের দাবিগুলো পূরণের চেষ্টা করতে পারেন। তবে ২০০৪ সালে যেভাবে ষাটের ওপর সাংসদ নিয়ে তাঁরা ইউ পি এ সরকারের কিছুটা নিয়ামক হতে পেরেছিলেন এবার বামশক্তি যতই সংহত হোক সারা দেশে ওই পরিমাণ আসন তাঁরা প্রত্যাশা করছেন বলে মনে হয় না। একই সঙ্গে টিএমসির ভূমিকা কী হবে তাও বিচার্য। টিএমসি দলের সঙ্গে কোনো নীতির যোগ আছে এত বড় ‘অভিযোগ’ আজ অবধি কেউ তুলতে পারেননি। তারা যেখানে সুবিধে সেখানেই যাবেন। ফলে ইন্ডিয়া জোটে যদি সিপিএম নিয়ামক হতে থাকে তাঁরা সেই ধার আর মাড়াবেন না —-- ইতিমধ্যেই সেই প্রসঙ্গ তাঁদের সুপ্রিমো তুলে দিয়েছেন। বিপরীতে টিএমসির কাছে যদি ভাল সাংসদ সংখ্যা থাকে ইন্ডিয়া জোটের কাছে তার ‘দরদাম’ ভাল হবে ও তাঁরা সেটাকে কাজে লাগাবেন সিপিএমকে দূরে রাখার জন্য। আর এটাও ঠিক রাজ্যের প্রদেশকংগ্রেস যাই বলুন দিল্লির হাইকম্যান্ড কখনো মমতার সঙ্গে সুসম্পর্ক ছেদ করেনি। মল্লিকার্জুন খড়্গে বারবার বিবৃতি দিয়ে ওঁকে কনফিডেন্সে রেখেছেন এমনকি অধীর চৌধুরীর প্রচারেও দিল্লির কেউ সেভাবে আসেননি। এই হিসেব ঠিক থাকলে ইন্ডিয়ায় মমতার ভূমিকা জোরদার হবে আর বাম সাংসদরা নিজেদের কর্মসূচি কী কতটা রূপায়ণ করতে পারবেন সেটা জিজ্ঞাসা চিহ্নের মুখে। এর পাশাপাশি মনে রাখা দরকার, আগামী দু-বছরের মধ্যে রাজ্যে বিধানসভার ভোট। অন্যদিকে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি, রেশন দুর্নীতি ও ওবিসি সার্টিফিকেট সংক্রান্ত রায় এখনো সুপ্রিম কোর্টে আংশিক চাপা পড়ে আছে। সেগুলি সামনে এলে রাজ্যের সরকারি দল হিসেবে টিএমসিকে তার মোকাবিলা করতে হবে। কেন্দ্রে বিজেপি থাকলে তাঁরা এখনকার মতোই স্বস্তিতে থাকবেন। কিন্তু ইন্ডিয়া জোট ক্ষমতায় এলে বামপন্থীরা চাইবেন এগুলোকে সামনে এনে নতুন করে জনমত গড়তে। এই জায়গাটায় টিএমসির একটা রক্ষাকবচ দরকার। তারা এতদিন বিজেপির থেকে মোটামুটি একটা আশ্বাস পেয়েছিলেন —- নতুন সরকারে যোগ দিলে সেই ‘কবচ’ তাঁরা আগেই জোগাড় করে নেবেন। সেক্ষেত্রে বামপন্থীরা কি কেন্দ্রের সরকারের থেকে খুব বেশি কিছু আদায় করতে পারবেন ? আরও একটা সম্ভাবনা হল, বিজেপি যদি অল্প কিছু আসনের জন্য ম্যাজিক ফিগার থেকে আটকে যায় তাঁরা কিন্তু টিএমসির সাহায্য চাইতে পারেন। এতদিন বিজেপি-বিরোধিতা করে তাঁদের পক্ষে কি বিজেপির হাত ধরা সম্ভব ? তাঁদের এযাবৎ ট্র্যাক রেকর্ড এর কোনো সদুত্তর দিতে পারে না। তবে একশো দিনের কাজ ও আবাস যোজনার যে প্রাপ্য টাকার কথা টিএমসি দল বারবার বলেন তাঁর কিন্তু এখনো কোনো নিষ্পত্তি হয়নি। কে বলতে পারে, ক্ষমতায় থাকার স্বার্থে বিজেপি সব পুরোনো প্রাপ্য মিটিয়ে দেওয়ার শর্তে টিএমসির সমর্থন আদায় করে নেবে না? তাঁর সুবিধে হল এখানে তিনি ‘রাজ্যের স্বার্থে’ কেন্দ্রের সরকারকে সমর্থন করছেন এরকম একটা একজিট রুট পেয়ে যাবেন খুব সহজেই। তাছাড়া, রাজ্যে বামপন্থীরা বেশি আসন পেলে তাঁর পক্ষে বিজেপির পাশে থাকাই সমীচিন। ভুলে যাওয়া উচিত হবে না, টি এম সি প্রতিষ্ঠালগ্নেই তিনি বলেছিলেন, বিজেপি তাঁর স্বাভাবিক বন্ধু ( ন্যাচারাল অ্যালি) । এই সমস্ত প্রশ্নেরই জবাব মেলার জন্য আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার অপেক্ষা।
জনতার খেরোর খাতা...
কবিতা - আছে কি উত্তর ? - Supriya Choudhury | আছে কি উত্তর ?—————সুপ্রিয়া চৌধুরী—————নেই হাওয়া নেই গাছের ছায়া নেই জল নেই আলোনতুন প্রজন্ম সামনে দাঁড়িয়ে প্রশ্নবাণে জর্জরিত তুমি- আছে উত্তর,-বলো ?কংক্রিটে ঢেকেছো ভোরের আকাশঢেকেছো সোনালী রোদ্দুর-সামনে তাকাও - দেখো ! চোখ খুলে সেই ভয়াবহ দিন নয় আর নয় বেশী দূর !!সবুজের ছোঁয়া খুঁজে ফেরে আজওএই যে ফেরারী মন-কি বলবে ? যবে মুখোমুখি হবে কচি কাঁচা যত অবুঝ মনেরে ? হয়েছে উন্নয়ন ?প্রগতির পথে ছুটছি আমরা, করবই বাজিমাৎ !শহরের যত সবুজ আঁচল সাফ করে দিয়ে চালিয়েই যাই উন্নয়নের করাত্। বুঝে নিতে হবে এসেছে সময়খুঁজে পেতে হবে উত্তরপ্রকৃতি সুরক্ষায় সচেষ্ট হয়ে হোক্ না উন্নয়ন !শুধু স্লোগানে ভর করে আর নয় চলা বিশ্ব পরিবেশ দিবসেই শুধু নয় বলা হবে সকলের দায় প্রকৃতি রক্ষা করাতবেই উত্তরসূরীরাও ফিরে পাবে এক দূষণ মুক্ত ধরা। —————হেদুয়ার ধারে - ১৪০ - Anjan Banerjee | বাসন্তীদেবী বললেন, ' মালতী সজনের ডাঁটাগুলো কেটেকুটে রাখ। কুমড়ো বেগুন আর বড়ি দিয়ে চচ্চড়ি করব। আলুটাও কেটে রাখিস। আর হ্যাঁ, দেখ তো রাঙালু আছে কিনা। থাকলে কেটে রাখিস ... আসছি আমি ... 'মালতী বলল, ' আমি করি না মা ... দেখবেন ভাল হবে ... '----- ' তুই করবি? বলতো কি ফোড়ং দিতে হবে? '----- ' কেন পাঁচফোড়ং ... '----- ' তোর মুন্ডু। এতে শর্ষে ফোড়ং লাগে ... '----- ' কেন আমরা তো পাঁচফোড়ং দিই। বেশ টেস হয় ... '----- ' ঠিক আছে তোর রান্না তুই বাড়ি গিয়ে টেস করবি। এখানে আজ আমি করব ... '----- ' আচ্ছা ঠিক আছে ... যা ভাল বোঝেন ... 'বাসন্তীদেবী বললেন, ' আমি চান করতে যাচ্ছি ... তুই এদিকে গুছিয়ে নে ... 'বলে পিছন ঘুরতেই দেখলেন সুমনা দাঁড়িয়ে আছে। এম এস সি- র মেরিট লিস্টে তার নাম উঠেছে। আজ অ্যাডমিশান।সুমনা বলল, ' মা, আমি বেরোচ্ছি। আজ ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডমিশান আছে ... 'বাসন্তী অত শত খবর রাখেন না। তার বিশেষ গরজও নেই। ছোট মেয়ে যতদিন না উপযুক্ত জায়গায় পাত্রস্থ হচ্ছে তার শান্তি নেই।তিনি বললেন, ' হ্যাঁ... তা বেরোচ্ছ বেরোও। এখন তো আর তোমায় পাহারা দেবার লোক নেই। তবে রাস্তা ঘাটে একটু হুঁশ তাল বজায় রেখ ... আর ওই ওটার কি হল? খুব তো বড় মুখ করে বললে ... '----- ' কোনটা বলতো .... '----- ' আরে ... ওই যে বললে, তুমি ওই জ্যোতিষীঠাকুরের খোঁজ বার করতে পারবে ... '----- ' ও হ্যাঁ, মনে আছে ... মনে আছে। এই অ্যাডমিশানের ঝামেলাটা মিটে গেলেই আমি ঠিক নিয়ে আসব বাবাজীকে ... চিন্তা কোর না ... '------ ' তাই নাকি? দেখা যাক তুমি কদ্দুর কি করতে পার ... '----- ' আমি আসছি মা ...বলে সুমনা বেরিয়ে গেল। সুমনা ইউনিভার্সিটির অফিস ঘরের সামনে গিয়ে দেখে প্রতিবিম্ব ওখানে একপাশে দাঁড়িয়ে আছে কাঁধে খাতা বইয়ের ঝোলা ঝুলিয়ে।----- ' কতক্ষণ এসেছ? ' সুমনা জিজ্ঞেস করে।----- ' এই মিনিট দশেক ... 'টাকা পয়সা, কাগজপত্র জমা দিয়ে অ্যাডমিশান পর্ব চুকতে ঘন্টাখানেক লাগল। ভাল ভিড় ছিল।প্রতিবিম্ব বলল, ' চল কফি হাউসে গিয়ে বসবে নাকি? '----- ' না না ... দূর ওখানে আমার ভাল লাগে না। যত আঁতেলের আড্ডা। আর অত সিগারেটের ধোঁয়া আমি সহ্য করতে পারিনা। তার চেয়ে চল ওদিকে হাঁটতে থাকি ওয়েলিংটন স্কোয়্যারের দিকে। এ রাস্তাটা দিয়ে হাঁটতে আমার দারুণ লাগে, কেন জানি না।'প্রতিবিম্ব বলল, ' আমারও। অগোছালো, অপরিচ্ছন্ন হলেও কেমন একটা প্রাণস্পন্দন আছে ... তাই না? '----- ' এগ্জ্যাক্টলি। প্রাণস্পন্দন আছে ... এটাই আমি বলতে চাইছিলাম। এটা বালীগঞ্জ বা ভবানীপুরে গেলে পাওয়া যাবে না। ' সুমনা বলে।----- ' একদম একদম ... 'তারপর বলল, ' তোমাকে বলা হয়নি ... আমি দুদিন টেস্ট ম্যাচ দেখতে গিয়েছিলাম ইডেন গার্ডেনে। আমার এক ক্লাসমেটের বাবা টিকিট দিয়েছিল। '----- ' তাই নাকি? জানতাম না তো ... '----- ' তোমার সঙ্গে তো বেশ কিছুদিন দেখা হয়নি ... '----- ' আমার বাপিও টিকিট পায় দু একজন ক্লায়েন্টের কাছ থেকে ... ইশশ্ আগে জানলে আমিও যেতাম ... '----- ' সেটা হল না। কপাল খারাপ। জয়সীমা যেদিন সেঞ্চুরি করল সেদিন আমি মাঠে ছিলাম। ওঃ ... কি অসাধারণ ব্যাটিং করল ... স্মিথ হিমসিম খেয়েছে ওকে রুখতে .... দারুণ ... প্রাইস আর টিটমাস কিচ্ছু করতে পারেনি । পরের দিন দেখলাম কাউড্রের ব্যাটিং। তবে কাউড্রে ভীষণ বোরিং ... খালি ঠুকুস ঠুকুস । ব্যাট করল বটে জয়সীমা ... আগুনে ব্যাটিং 'ওরা সদ্য সমাপ্ত ভারত ইংল্যান্ড ক্রিকেট সিরিজের কথা বলছে। পতৌদির ভারত আর মাইক স্মিথের ইংল্যান্ড। 'ওরা হাঁটতে হাঁটতে ভীম নাগের দোকানের সামনে পৌঁছল।সুমনা বলল, ' মিষ্টি খাবে নাকি? '----- ' হ্যাঁ তা খেলে হয় দুটো করে লেডিকেনি ... '---- ' না না লেডিকেনি না, রসমাধুরী খাব ... ' সুমনা বলল।----- ' রসমাধুরী কিন্তু চার আনা করে পড়ে যাবে ... '----- ' আচ্ছা চল তো ... ম্যানেজ হয়ে যাবে ... 'প্রতিবিম্বকে টেনে নিয়ে সুমনা ভীম চন্দ্র নাগের মিষ্টির দোকানে ঢুকল।চার আনা করে পড়ল বটে, মিঠাইয়ের মনোরম মাধুরী কিন্তু প্রথম প্রেমের আস্বাদের মতো দেহে মনে চারিয়ে গেল।দোকান থেকে বেরিয়ে সুমনা বলল, ' চল ওয়েলিংটন স্কোয়্যারে গিয়ে একটু বসি ... '----- ' আচ্ছা চল ... 'ওরা পার্কে ঢুকল। যত অলস লোক ওখানে বসে আছে নিশ্চিন্তমনে। দু একজন নিশ্চিন্তে ঘুম দিচ্ছে। সুমনা আর প্রতিবিম্ব ওর মধ্যেই জায়গা করে এক পাশে বসল।সুমনা বলল, ' এই শোন, একটা কথা মনে পড়ে গেল। আমার মা তো জ্যোতিষীঠাকুরের দেখা পাবার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছে। আমি মাকে কথা দিয়েছি যেখান থেকে হোক খুঁজে নিয়ে আসব। যা হোক একটা ব্যবস্থা কর। আমার বিয়ের ব্যাপারটাও পাকাপাকি জানিয়ে দাও ... এ তো আর সহ্য হচ্ছে না ... '----- ' ওঃ ... কি বিপদ ... আবার সেই ঝঞ্ঝাট ! '----- ' কি করবে বল, তোমার ভাগ্য। নইলে আমার সঙ্গে জড়িয়ে পড় ... তবে এবার ফাইনাল। আবরণ পুরো উন্মোচিত করে দাও এবার। '---- ' আমিও ওরকমই ভাবছি।----- ' ভাব ভাব ... ভাল করে ভাব। কবে বলব তা'লে? '----- ' সামনের রবিবার বল। স্যারও সেদিন বাড়ি থাকবেন ... '----- ' হ্যাঁ .... সেই ভাল। বাপিকে বলে রাখব। 'রাত্রি জোর পায়ে হেঁটে বটতলা থানার সামনে পৌঁছল। তার হৃদপিন্ড এখনও জোরে ছুটছে। দেখে থানার সামনে সাগর দাঁড়িয়ে আছে।রাত্রি সাগরের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।সাগর বলল, ' এই ... কালীবাবুর জন্য দাঁড়িয়ে আছি। কালীবাবু মানিকতলার দিকে গেছে। এরা বলছে এক্ষুণি ফিরবে ... কি হল, এত হাঁফাচ্ছ কেন? '----- ' বলছি বলছি ... 'রাত্রি ঘটনার বর্ণনা দিল এবং সন্তোষ দাসের কীর্তিও জানাতে ভুলল না।সব শুনে সাগর বলল, ' ও বাবা ... এ তো ভাল নাটক ... '---- ' তুমি এটাকে নাটক বলছ? '---- ' আমাদের জীবনে যা ঘটে সবই তো নাটক ... ' সাগর দার্শনিক ভঙ্গীতে বলল।----- ' সে তো ঠিকই, তবে এরকম উটকো নাটক ঘাড়ে এসে পড়লে তো খুব সুখের ব্যাপার না ... '----- ' না, তা না ... তবে সাগর মন্ডলের ইয়ে হয়েসুখে থাকার আশা আছে বলে মনে হয়? দেখ ... এখনও সময় আছে, ভাল করে ভেবে দেখ ... '----- ' চুপ কর তো ... সিরিয়াস ব্যাপার নিয়ে ঠাট্টা ইয়ার্কি ভাল লাগে না ... '----- ' আরে ... আমি এই তো সবে শুনলাম। সন্তোষের কাছে কেসটা কি শুনি, তারপর তো ... আসলে লোকদুটোকে কে লাগিয়েছে সেটা জানাটা সবচেয়ে জরুরী। দাঁড়াও আগে সন্তোষের পাত্তা লাগাই ... ওই তো কালীবাবু আসছে। তুমি কি এখানে একটু বসবে, নাকি বাড়ি চলে যাবে? '----- ' পাঁচ মিনিট বসে যাই, নইলে উনি কি মনে করবেন ... ' রাত্রি বলল।---- ' সেই ... কালীবাবুর মন মেজাজ ভাল নেই। সামনের মাসে রিটায়ারমেন্ট। আমার একটা ভাল বন্ধুকে আর পাব না ... 'রাত্রির বুকের ভিতর থেকে একটা গভীর শ্বাস বেরিয়ে এল।বলল, ' আরও কত বন্ধু হারিয়ে যাবে জীবনের রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ... 'হনহন করে হাঁটতে হাঁটতে কালীবাবু এসে পড়লেন।বিব্রত কন্ঠে বললেন, ' আরে ... এখানে খাড়ায়ে কেন, ভিতরে বসলেই তো পারতেন ... আসেন আসেন ... 'ভিতরে ঢুকে নিজের চেয়ারে বসে চায়ের অর্ডার দিলেন।তারপর বললেন, ' আর তো হয়েই আসল। আর কয়দিন বাদেই তো বাই বাই গুডবাই ... তখন আর আমারে কেই বা মনে রাখবে। এই থানার বাইরে আমার আর কেই বা আসে। সামাইন্য মানুষ আমি ... 'রাত্রি বলল, ' আপনাকে আমরা মনে রাখি কিনা সেটা আপনি পরীক্ষা করে নেবেন। কর্ত্তব্য আমাদের, বিচার সম্পূর্ণ আপনার ... 'সাগর বলল, ' মা কি কসম ... 'কালীবাবু পকেট থেকে রুমাল বার করে চোখে চাপা দিলেন। কেন কে জানে। বোধহয় চোখে কিছু পড়েছে।( চলবে )********************************************ভাতা, ভিক্ষা, বামফ্রন্ট এবং নব্য বামপন্থা - Eman Bhasha | #ভিক্ষা #ভাতা নিয়ে এত কথা। প্রথম বামফ্রন্ট সরকারের কাজ পড়ুন। এমনি এমনি ৩৪ বছর ক্ষমতায় ছিল না!সে সব কথা কেন যে আজ কেউ বলে নাইমানুল হকঘটনা-১।।১৯৭৫ এর এক রাত। মাঝরাতে ঘুম ভেঙ্গে যায় ৯ বছরের এক বালকের। ঘুম ভাঙ্গা চোখে দেখে, মা ব্যস্ত একটি বালিশ ছিঁড়তে। বালিশটি ছিঁড়ে তার মধ্যে পুরে সেলাই করে দেওয়া হচ্ছে লাল রঙের একটি পতাকা। আর বড়দা এবং মেজদি ব্যস্ত দেওয়ালের ওপর ইংরেজি হরফে লাল রঙে লেখা ‘সি পি এম’ শব্দটি মুছতে। কোনদিন মেজদি নিজের খেয়ালে লিখেছিল, শব্দটি। খবর এসেছে আজ রাতে আবার সি আর পি আসতে পারে। ছেলেটির বাবা ছিল রাজনীতির কারণে ফেরার।কয়েকদিন পর বাড়িতে এল একটা চিঠি। লাল রঙের। ক্রোকের নোটিশ। ব্যাঙ্কের। গ্রামের ্কিছু সম্পন্ন চাষী এক ফসলি জমিতে দুবার চাষ করবে বলে শ্যালো (অগভীর নলকূপ) বসিয়েছিলেন। রাস্টন, কির্লোস্কার এর তৈরি সে সব শ্যালো ‘ফেল’ করে যায়। জল ওঠে না। চাষীর স্বপ্ন পূরণ হয় না। কিন্তু ব্যাঙ্কের ঋণ বেড়ে যায় সুদে আসলে। আসতে থাকে চিঠি, জমি ক্রোকের। এর পাশাপাশি আসতে থাকে সরকারি চিঠি। দাদা পড়াশোনার জন্য বাইরে। বালকটি পেত ডাক হরকরা বা চৌকিদারের হাত থেকে চিঠি । তার রং –ও লাল। তাতেও বকেয়া খাজনা এবং জল কর না দিলে ক্রোকের হুমকি।লাল রঙ্-এ তাই আতঙ্ক ধরে যায় বালকটির। ঘটনা -২।।ভাদ্র মাস। প্রচন্ড গরম। গ্রামে ঘরের দাওয়ায় বসে আছেন ১০-১২ জনের একটি দল। কাজ চান তাঁরা। কাজ না দিতে পারলে অন্তত সের খানেক চাল বা গম। বাকিরা উঠে চলে যান, কিছু না কিছু নিয়ে। একজন কেবল বসে থাকেন কিছু না বলে। সুদর্শন, গায়ের রঙ সাহেবদের মত দুধে আলতা। রোদে পুড়ে অন্যরকম দেখাচ্ছে। --কি খবর রে মাফুজ? জিজ্ঞেস করেন, বালকের মা।মাফুজ মৌন, নিরুত্তর। অনেক তাগাদায় জানা যায়, মাফুজ কাজ করতেন কলকাতায় বেঙ্গল পটারিতে। কারখানা লক আউট। বাড়ি ফিরেছেন, তিনদিন খাওয়া নেই। কাউকে বলতে পারেন নি। তাই আজ বাড়ির লোকের কথা ভেবে এসেছেন এ বাড়িতে। যদি কিছু গম মেলে, নুন দিয়ে ‘জাউ’ করে খাবেন। মাফুজ বলতে পারেন না, আর। চোখের জল টপটপ করে গড়িয়ে পড়ে। চাল নিয়ে ফেরেন তিনি, এর পরে।ঘটনা ৩।।১৯৭৬। ছেলেটি ক্লাসে প্রথম হয়। তবু তার চিন্তা যায় না। সাফল্যের দুশ্চিন্তা অনেক বেশি। ফল বের হওয়ার দিন নাম ডাকা হচ্ছে। সেকালের প্রথা অনুযায়ী শেষ থেকে ডাকা। দ্বিতীয়-র নাম ও ডাকা হয়ে যায়। তার নাম আর ডাকা হয় না। কিন্তু সে বুঝতে পারে, সে প্রথম হয়েছে। কারণ প্রথমের নাম ডাকা হয়নি। তার মাইনে জমা পড়েনি। এবার শুখার বছর। প্রথম হয় বলে তিন মাসের মাইনে আর পরীক্ষার ফি কেবল দিতে হয়। বছরে ২৬ টাকা ৭৫ পয়সা। দরদর করে চোখের জল গড়িয়ে পড়ে। প্রগতিপত্র বা মার্ক শিট দেওয়ার অনুরোধও সে করে উঠতে পারে না।৪আজ যখন ৩৪ বছরের ‘অপশাসনে’র কথা ওঠে তখন বালক বয়সের কথা মনে পড়ে। ১৯৭৭-এ একটি সরকারের ক্ষমতায় আসা কীভাবে বদলে দেয় মানুষের জীবন। ব্যাঙ্ক ঋণ মকুব হয়, মকুব হয় বকেয়া খাজনা, শুধু তাই নয় তিন একর পর্যন্ত জমির খাজনা মকুবের আদেশ শুনিয়ে যান, ‘আপনারা সবাই শোনো’ বলে মুকুন্দ চৌকিদার। দশম শ্রেণি পর্যন্ত বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ মেলে গরিব, মধ্যবিত্ত, বড়লোক – সব ঘরের ছাত্র-ছাত্রীর। লাল রং আর আতংকের থাকে না।্ প্রিয় হয়ে ওঠে অন্য লাল। বাম আমলে জ্যোতি বসু-র সরকারে অশোক মিত্রের অর্থমন্ত্রিত্বে ঘটে এই ঘটনা। সে সব কথা কেন যে আজ কেউ বলে না!গ্রামে খুব কম মানুষ ছিলেন যাঁরা ছেলে মেয়েদের বছরে দু’বার জামা কাপড় কিনে দিতে পারতেন। সরপি দেওয়া, তালি মারা, রং চটা, সেলাই করা পোশাক ছিল স্বাভাবিক ঘটনা। জুতো পরে বিদ্যালয়ে আসতে দেখা যায়নি, ছোটবেলায়। সেটা ছিল বড়লোকিপনা। একজন সপ্তম শ্রেণিতে জুতো পরে বিদ্যালয়ে আসায় ছেলে-মেয়েরা তো বটেই স্যাররাও ‘বাবু’ বলে হাসি ঠাট্টা করেন। সে সময় ১৯৭৭ থেকে মেয়েরা বিদ্যালয়ে এলে দু প্রস্থ করে পোশাক পেতে থাকে। সবুজ স্কার্ট, সাদা জামা। (লাল নয়, সবুজ রং)। মেয়েরা জামা পাবে বলে বিদ্যালয়ে আসতে শুরু করে বেশি সংখ্যায়। রাজ্যে এমনি এমনি নারী শিক্ষা বাড়েনি। গ্রামে ১৯৭৭- এর আগে দিন মজুরি করে পাওয়া যেত দিনে ৮০ পয়সা থেকে এক টাকা মানে মাসে ২৪ থেকে ৩০ টাকা। আর এক সের চাল। সে চালের সেরের তলায় আবার অনেক মালিক কাদা দিয়ে রাখত। কার্যত ৫০০-৬০০ গ্রাম চাল মিলতো। সবদিন কাজ মিলত না। না খেয়ে কাটত বছরের বেশির ভাগ দিন। খাওয়া বলতে গেঁড়ি গুগলি চুনো মাছ, আঁদাড়ে পাদাড়ে বনে বাদাড়ে থাকা মেটে আলু, কচু, ওল, শুসনি, কলমি শাক, শাঁপলা সেদ্ধ, আর কখনো সখনো ফ্যান ভাত, খুদ ভাঙ্গার খিচুড়ি, মাইলো-যব-গমের জাউ, ( আজ যা বড়লোকের মেদ কমানোর জন্য ওটস জাতীয় খাবার)। ধান রোয়া আর কাটা ছাড়া কাজ কই? বছর ভর কৃষাণের কাজ তথা বাঁধা মাইনের কাজে মিলতো ২০০ টাকা আর ১২ মন ধান। কিন্তু সম্পন্ন গ্রামেও ১০-১২ জনের বেশ লোকের কৃষাণ রাখার ক্ষমতা ছিল না। অনেক সম্পন্ন চাষিকে দেখেছি ছোটবেলায়, কার্তিকের শেষ আর অগ্রহায়ণের শুরুতে নিজেদের মধ্যে নতুন ধান বিনিময় করতে। ধান কাটার পর জমিতেই ঝেড়ে অন্যকে ধার দেওয়ার প্রথা। তার ধান উঠলে সে আবার অন্যকে দেবে। সারা বছর ধানের মরাই (গোলা) বাঁধা থাকতো এমন চাষি এক শতাংশের বেশি ছিল না। যারা সুদে টাকা খাটাত তারা অবশ্য একটু ভাল অবস্থায় ছিল। সে সময় বামফ্রন্ট সরকার ঠিক করে তপশিলি জাতির ছেলে মেয়েরা বিদ্যালয়ে এলে মাসে ২০ টাকা করে পাবে। বছরে ২৪০ টাকা। মাসে মাসে মিলতো না। বছরে দুবার। ১২০ টাকা করে। আজকে ভাবা যাবে না, কিন্তু ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে গরিব ঘরে একসঙ্গে ১২০ টাকা অনেক টাকা। এক থেকে দেড় কুইন্টাল চাল কেনা যায়। ২ থেকে ৪ কাঠা জমি কেনা যায়। বাবা মা দেখলেন, বাগালি করার থেকে বিদ্যালয়ে পাঠালে রোজগার বেশি। সম্ভবত ১৯৮০ থেকে শুরু হল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে টিফিন দেওয়া। কোথাও পাউরুটি-কেক। কোথাও অন্যকিছু। কিছু জায়গায় কিছু অনিয়মের খবর এলেও এতে সাড়া পাওয়া যায় ভাল। খাবারের জন্যও অনেকে পড়তে এল। খালি পেটে বিদ্যে শিক্ষে হয় না, এটা অনেক মধ্যবিত্ত স্বার্থপর লোক বুঝতে চান না। (যদিও মুনি ঋষিরা বুঝতেন – ‘অন্নই ব্রহ্ম’ গল্প তার প্রমাণ)। খাবার দেওয়াটা জরুরি। আজকের দিনের ‘মিড ডে মিল’ এর অনেক আগে প্রথম বামফ্রন্ট সরকার এই কাজ শুরু করেছিল।৫সংখ্যালঘু ছাত্র-ছাত্রীদের কোন বৃত্তি আগে দেওয়া হতো না। বাম আমলেও হয়নি। কিন্তু পড়তে আসার সংখ্যা বাড়ল। কারণ খেতমজুরদের ন্যূনতম বেতনের দাবিতে বহু ধর্মঘট হয়। দু টাকা আর দু কেজি চালের দাবি জয়যুক্ত হয়। কিন্তু বহু জায়গায় কার্যত মেলে দেড় টাকা আর দেড় কেজি চাল । খেতমজুরদের একটা বড় অংশ ছিলেন সংখ্যালঘু। আর এর পাশাপাশি পঞ্চায়েতের উদ্যোগে রাস্তা তৈরি, পুকুর ও নর্দমা সংস্কার বা নির্মাণ, খেলার মাঠ তৈরির মত নানা কাজ শুরু হয়। ‘কাজের বিনিময়ে খাদ্য’ প্রকল্পে গম মেলে। সততার সঙ্গে, হ্যাঁ সততার সঙ্গে, বহু গ্রামে কাজ হয়। এমনও হয়েছে ৩০০ টাকা এসেছে, কাজ হয়েছে ৩০০০ টাকার। গ্রামের সব মানুষকে নিয়ে। অন্য দলের মানুষ প্রথমে অনিচ্ছুক থাকলেও যোগ দিয়েছেন, রাস্তা নির্মাণে। তাঁদের কাউকেই কোষাধ্যক্ষ করা হয়েছে। এমনি গ্রামের চেহারায় বদল হয়নি। আজ বোঝা যাবে না, গ্রামের রাস্তা কি ছিল? এক হাঁটু কাদা বর্ষা থেকে আশ্বিন মাস পর্যন্ত। তাই, মানুষ স্বেচ্ছাশ্রম দিয়েছেন। খেতমজুররা মজুরি নিয়েছেন, মধ্যবিত্ত যুবক গরুর গাড়িতে কাটা মাটি এনে ফেলেছেন, কোদাল চালিয়ে বহু মাটি সমান করেছেন। এ যেন ছিল চিন চিং মাই-এর চিনা উপন্যাস, ‘বিপ্লবের গান’-এর এক ক্ষুদ্র সংস্করণ। বামপন্থী ছাত্র সংগঠন ও নেতা এবং প্রিয়ব্রত দাশগুপ্তদের মত আদর্শবান কিছু অধ্যাপকের অবদানও না বললে অন্যায় হবে। এরা এন এস এস-এর নামে বহু গ্রামে পড়ে থেকে, মশার কামড় খেয়ে রাস্তা তৈরি করেছেন। শুধু সেমিনার করেন নি। ৬আমার বলার কথা এই, খেতমজুররা খাবার ও জমি পেলে ছেলে মেয়েরা পড়তে এল। (প্রসঙ্গত, পশ্চিমবঙ্গে সি পি এমের খেতমজুর সংগঠন ছিল না যাঁরা বলেন, তাঁরা তথ্য বিভ্রান্তির স্বীকার, খেতমজুর সংগঠন ৮০-র দশকের শুরুতেও ছিল। ১৯৭৮-এ গড়ে ওঠে)। বছরে দু’ মাস কাজ মিলত, বাম জমানায় মিলল প্রথমে ছয় মাস। পরে সারা বছর। এখনো বহু গ্রামে সহজে খেতমজুর মেলে না। আর আগে সংখ্যালঘু মানসিকতা ছিল পড়ে কোন লাভ নেই, চাকরি দেবে না। বামপন্থীদের জাতপাতহীন ধর্মনিরপেক্ষ মানসিকতা এ ভাবনায় খানিকটা বদল আনে। ফলে তাঁদের ঘরের ছেলে-মেয়েরাও পড়তে এল। আগে গ্রামে সংখ্যালঘু পরিবারে মধ্যবিত্ত হলে ১৩- ১৪ , গরিব হলে ১১-১২ বছর বয়সেই বিয়ে দিয়ে দেওয়া হতো। ‘হিন্দু’ পরিবারে এই বয়স ছিল যথাক্রমে ১৬-১৭, ১৩-১৪। এখন এটা ভাবাই যাবে না। ১৮ বছরের আগে বিয়ে খুব কম জায়গাতেই হয়। কুড়িতেই বুড়ি—এই শ্লোগান অচল করে দিয়েছিল বামফ্রন্ট সরকার। ২৪-২৫ বছর বয়সে বিয়ে এখন স্বাভাবিক ঘটনা। ‘অরক্ষণীয়া’র দিন শেষ করায় বামপন্থীদের ভূমিকার কথাও কেউ বলে না। প্রথম দিকে পণ নেওয়ার বিরুদ্ধে প্রচারে কাজ হয়েছিল। পরে অবশ্য তা অদ্ভুতভাবে বদলে গেল। এছাড়া আরেকটা বিষয় বলা দরকার, গরিব আদিবাসী বা তপশিলি জাতিভুক্ত মানুষের পাড়াগুলোতে মদ্যপান ছিল স্বাভাবিক ঘটনা। তার বিরুদ্ধেও প্রচার চলে। এর ফলও ফলে। এবং প্রতিবেদকের অভিজ্ঞতা এখন এই, আদিবাসী তপশিলি পা|ড়ায় মদ খায় হাতে গোনা লোক, এর চেয়ে সাধারণ মধ্যবিত্ত যুবকরা মাতাল বলে পরিচিতি না পেলেও মদ খায় অনেক বেশি। পূজা পার্বণ উৎসব মানেই একদলের কাছে মদ গাঁজা নেশার বাহানা। শিক্ষিতের হার তপশিলিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়েছে। একই কথা প্রযোজ্য সংখ্যালঘুদের ক্ষেত্রেও। আর নারীশিক্ষার হারে তো লক্ষ্যণিয় উন্নতি বাংলায়।৬বামফ্রন্ট ১৯৭৭-এর পর ক্ষমতায় আসার পর খাস জমি দখল ও বিলির আন্দোলন চলে। এতে বহু প্রান্তিক ও ভূমিহীন মানুষ জমির অধিকার পান। সমবায় পদ্ধতি চালুর চেষ্টাও হয়। এই প্রতিবেদক নিজে বর্ধমানের খন্ডঘোষ থানার কামদেবপুর গ্রামে চাষিদের মধ্যে সমবায় প্রথায় চাষ নিয়ে উন্মাদনা প্রত্যক্ষ করেছে। কিন্তু কেন তা ঝিমিয়ে পড়ল, তা গবেষণা ও শিক্ষার বিষয়। বুদ্ধিমান ও প্রতিভাবান ছেলেদের মধ্যে একজনের জন্য খুব আফশোস হয়। গেঁড়া (ভাল নাম মনে নেই)। প্র্য়াত বড়দির শ্বশুরবাড়ির গ্রামের ছেলে। তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ত। ১৯৭৪-এ। গেঁড়ার বাবা মারা যাওয়ায় তার পড়া বন্ধ হয়ে যায়। বাগালি করে দিন কাটে। গেঁড়ার অংকে ছিল দারুণ মাথা। যখন সমবায় প্রথায় চাষ শুরু হল, ১১ বছরের গেঁড়ার কি বিপুল উৎসাহ। দিন বদলের পালার স্বপ্নে সে বিভোর। চাষীদের গড়া মাচা এবং ঘরে গভীর রাত পর্যন্ত কাটিয়েছি, তার সঙ্গে । (গ্রামীণ মধ্যবিত্ত পরিবারে এ স্বাধীনতা আর বালকদের নেই। পড়া বা টিভি-র ঠেলায় এখন সব অলীক )। ৭যে মানুষ খেতে পায়, সে তার ছেলে মেয়েকে নিরক্ষর রাখতে চায় না। প্রথম শ্রেণিতে পড়ার সময় আমাদের সঙ্গে পড়ত ১৫৭ জন ছেলে মেয়ে। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ। ক্লাসে প্রথম দ্বিতীয় হতো মেয়েরা। ( পরে তারা আর তৃতীয় বা চতুর্থ শ্রেণির পর দারিদ্রের কারণে পড়েনি)। দ্বিতীয় শ্রেণিতে সেটা দাঁড়াল ৪৬। তৃতীয় শ্রেণিতে ৩৭। চতুর্থ শ্রেণিতে ১৭। আর বৃত্তি পরীক্ষার পর ১৫ জন। এর মধ্যে ৯ জন মাধ্যমিক পর্যন্ত যায়। আমাদের গ্রামের সেই প্রথম সঙ্গে এতজনের মাধ্যমিক পড়তে যাওয়া। ১৯৮০তে।গ্রামে জুনিয়ার হাইস্কুল ছিল। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত। মোট ছাত্র ছিল, চারটি ক্লাশ মিলিয়ে ৬৭ জন। নবম শ্রেণিতে পড়তে যেতে হয়েছে ৬ কিমি দূরের বিদ্যালয়ে। গ্রীষ্মকালে সাইকেল। বর্ষায় যাওয়া আসায় ৬/৬ মোট ১২ কিমি রাস্তা হাঁটা।(বিশ্বাস হবে কিনা জানি না, গ্রামে তখন মোট সাইকেল ছিল ১২টা। ১৯৮০ সালে। আজ চারচাকা গাড়ির সংখ্যা অন্তত ৫০ টি। ঘরে ঘরে মোবাইল। টিভি। সাইকেল তো এখন বাড়ির মেয়েরাও চড়ে। ফলে একাধিক সাইকেল তো আছেই। গ্রামে লোকে কুটুম বাড়ি যেতে ফুল প্যান্ট ধার করতো। ঘড়ি চেয়ে নিয়ে যেত। ইস্ত্রি ছিল বড় জোর ৪-৫ টি বাড়িতে। সাইকেল চাওয়া তো ছিল আকছার ঘটনা।) গ্রামে আজ জুনিয়ার হাইয়ের বদলে মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সেখানে চার শতাধিক ছাত্র।৮না খেতে পাওয়া লোক নেই। কাজের লোক পাওয়া খুব কঠিন। গৃহ পরিচারিকা ছোট বেলায় খুব সহজেই মিলতো। লোকে রাখার জন্য সাধাসাধি করতো। আজ কলকাতার থেকে বেশি টাকা দিয়েও পাবেন না। (সৌজন্য, ১০০ দিনের কাজ। সে শহুরে বাবুরা যত গালই পাড়ুন, এর বিরুদ্ধে)। মেয়েরা পড়ছে। এ পড়া ১৯৭৭-এর পর জোরদার। কারণ নতুন পোশাক শুধু নয়, বাবার কাছে পয়সা আসা। আর আত্মসচেতনতা ও আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি, যা বামপন্থীদের অবিস্মরণীয় আদর্শবাদী প্রচার ও শিক্ষার ফসল।খেতমজুর আন্দোলন, খাস জমি বিলির পাশাপাশি অপারেশন বর্গা, পঞ্চায়েত ব্যবস্থা আর প্রাথমিকে ইংরেজি না থাকার কথা বলতে হবে। প্রাথিমকে ইংরেজি না থাকায় পড়াশোনার ভীতি কেটে গরিব ঘরের প্রথম প্রজন্মের ছেলে মেয়েরা বিদ্যালোয়ে আসে। ব্দলে যায় গ্রামের অর্থনীতির মাঞ্চিত্র। আর গরিব কে মিথেয় দলিল লখে ঠকানো যায় না। ৫০ টাকাকে ৫০০০ বানানো যায় না। নিজে অংক কষতে পারে বলে ধান চাল ডিম মুদি মনোহারি পোশাকের ব্যবসা করে অনেকে পয়সার মুখ দেখে। বিভূতিভূষণের ‘ইছামতী’র বহু নালু পাল-রা এখন বাস্তব।৯ইংরেজি দেখিয়ে দেবে কে? ক্লাসে প্রথম দ্বিতীয় হওয়া মেয়েরা বিদায় নিল অভাব আর ইংরেজির চাপে। যাদের ঘরে ভাত ছিল, তাদের ঘরের ছেলেমেয়েরা সেই স্থান নি্ল। আজকের বিচারে বিধান বাবুদের কি দশা হতো কে জানে। ইংরেজির মাস্টারমশাই ছিলেন বিধানবাবু।আর বাবা-মা রা মাস্টার মশাইকে বলতেন, খুব করে মারবেন, পড়া না পারলে। (আজকে?)বিধানবাবু যাকে মারতেন তাকে দিয়েই বাঁশ ঝাড় ( পাশেই ছিল আমাদের বাঁশ ঝাড়) থেকে অনেক সময় ছড়ি কাটিয়ে আনাতেন। তার পিঠ লাল না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত থামতেন না। মারতে মারতে বেত ভেঙ্গেও ফেলতেন। সেই জন্য দারুণ মাস্টার হিসেবে তাঁর অভিভাবক মহলে খুব খ্যাতি ছিল। কেউ নালিশ কোন দিন তো করেন নি, উলটে জানতে পারলে, দেখা হলে বলেছেন, ‘মাস্টার মশাই বেশ করেছেন, ঠেঙ্গিয়েছেন, পারলে আরো ঠেঙ্গাবেন, যদি মানুষ হয়’ (লক্ষ্যণীয়, বড়ো নয়, মানুষ)। আর ছেলে-মেয়েদের মধ্যে ছিল প্রবল ভীতি। প্যান্টে পেচ্ছাপ করে ফেলতে দেখেছি। তৃতীয় শ্রেণিতে যখন পড়ি, দেখি, একজন চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রীকে হাত ধরে ঘোরানো হচ্ছে পড়া না পারার জন্য, আর ভয়ে তার পেচ্ছাপ ছড়িয়ে পড়ছে চারপাশে বৃত্তাকারে। এ নিদারুণ দৃশ্য প্রাথমিকে ইংরেজ পড়ানোর কথা বললেই মনে আসে। সেই মেয়েটি আর পরদিন থেকে লজ্জায় বিদ্যালয়ে আসেনি। [যাঁরা প্রাথমিকে ইংরেজির জন্য কেঁদে ভাসান তাঁরা খোজ নেবেন, আজো গ্রামে (শহরেও) ভাল ভাবে ইংরেজি দেখিয়ে দিতে পারেন, এমন মানুষ কজন আছেন! (প্রসঙ্গত ১৯৯৯ থেকে আবার প্রাথমিকে ইংরেজি চালু হয়েছে। আর শহর-বাজারে ইং-মিডিয়ামের ছড়াছড়ি। বহু সুপন্ডিত থাকার কথা!)]১০চাষীর ছেলেদের ’বাঁকা কলম’ তথা লাঙ্গল ঠেল গে যা’ ব্যঙ্গ করতেও শুনেছি মাধ্যমিক পড়ার সময় দু একজন মাস্টার মশাইকে। কিন্তু বামপন্থী আন্দোলনের প্রভাবে এ ব্যঙ্গ পরে বন্ধ হয়ে যায়। এই ব্যঙ্গ বন্ধের পিছনে আজ বুঝি, প্রভাব ছিল ‘সহজপাঠ’ নিয়ে আন্দোলনের। কেন জেলেকে বা চাষিকে আপনি সম্বোধন হবে না—সে নিয়ে তর্ক তুলেছিলেন বামপন্থীরা। বাংলার সামাজিক আর্থিক বদলের ইতিহাসে ‘সহজপাঠ’ আন্দোলনের প্রভাব আলোচিত হওয়া দরকার। পার্থ চট্টোপাধ্যায়রা যদি নজর দেন।১১বন্যা হলেই একদল মানুষকে হাতে আঁকা সাপ আর মানুষের খড়ের চাল বা গাছে সহাবস্থানের ভীতিপ্রদ ছবি নিয়ে ভিক্ষে করতে দেখা যেত। ১৯৭৮ এর ভয়ংকর বন্যার পর কিন্তু একজনকেও ভিক্ষে করতে আসতে দেখা যায়নি। বরং গ্রামের মানুষ জল কমলে বের হন পঞ্চায়েত সদস্য বা স্থানীয় বামপম্থী নেতৃত্বের আহ্বানে ত্রাণ সংগ্রহ করতে। অন্যদের বিপদে পাশে দাঁড়ানোর এ নজির ভুলে যাওয়া লজ্জার। আজকাল প্রায় সবাই সরকারের ভরসায় বসে থাকেন, সেটার বিপরীত ছিল এই ঘটনা। বাবার সঙ্গে ঘুরেছি গ্রামে ত্রাণ সংগ্রহে। দানের এক বিপুল সাড়া দেখেছি তখন। ১২ বছর বয়স। মুড়ি-চিঁড়ে-চাল নিয়ে আমাদের প্রিয় এক কর্মী মানুষ আর কালামের সঙ্গে গিয়েছিলাম ১৩-১৪ কিমি দূরের সুবলদহ গ্রামে (বিপ্লবী রাসবিহারী বসু-র পিতৃভূমি)। বন্যা কত ভয়ংকর হতে পারে, উঁচু এলাকার মানুষের সেই প্রথম দেখা। গিয়ে দেখি চারপাশ জলমগ্ন। প্রায় তিন কিমি রাস্তা সাঁতরে আসতে হয়েছে। ভাবছি সবাই না খেয়ে বসে আছে। গিয়ে দেখি খাদ্যের হাহাকার নেই। কারণ সরকারি ত্রাণ পৌঁছেছে আগেই। পার্টির লোকেরাও সবাই আছেন। কেজি খানেক সাইজের রুইমাছ মাছ বিক্রি হচ্ছিল ৫০ পয়সা কেজি। কিন্তু ক্রেতা ছিল না। বানের জলের মাছ বলে।ভিখারি গ্রামে আগে ছিল ভালই। এখানে গ্রামে ভিখারি অনেক কম। ৮০-র দশক থেকেই ভিখারি কমতে থাকে। শহরে বেড়েছে। কিন্তু ‘তিন দিন খাইনি’ বলে দুঃখী কণ্ঠস্বর খুব কম গ্রামেই শোনা যায়।১২গ্রামে ভিখারি কমার পিছনে আছে প্রথম বামফ্রন্টের একটি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত। গরিব দুঃস্থ বয়স্কদের জি আর বা জেনারেল বিলি। চাল বা গম দেওয়া হতো মাসে মাসে। ১০ কেজি করে। কারা জি আর পাবে সেটা প্রথম দিকে দেখেছি, গ্রামের মানুষদের বৈঠকে ঠিক হতো। পরে চলে যায় পার্টি ব্রাঞ্চের হাতে। এটা না গেলেই মঙ্গল হতো। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে গ্রামের মানুষের বৈঠক ডাকলে মাঠ ভর্তি হয়ে যেত। মতামত চাওয়া হতো সবার। পরে পার্টির খবরদারি বেড়ে যাওয়ায় জমায়েত কমে গেল। লোকে জানত, মিটিং লোকদেখানি। সিদ্ধান্ত আগেই হয়ে আছে। ফলে মানুষ ক্ষুণ্ণ হয়ে আসা প্রথমে কমালেন। ৯০ দশক থেকে বিরল হল। গ্রাম সংসদ গড়েও তত কাজ হল না।১৩১৯৬৭-এর যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে প্রথার অবসান ঘটেছিল বহু গ্রামেই। রবীন্দ্রনাথের ‘শাস্তি’ গল্পে ছিদাম-দুখিরাম দুই ভাইয়ের বেগার খাটতে যাওয়ার কথা পাঠকের মনে পড়তে পারে। যত গাল খেয়েছিল তত খাবার জোটে নি, খাবার না খেয়েই তো মাথা গরম দুখিরামের। খুন করেই ফেলে বউ রাধাকে। যার জেরে মিথ্যা দোষে জা চন্দরাকে যেতে হয় জেলে। ১৯৭৭-র পর অবসান ঘটে আরেক বিষ প্রথা গতর বন্ধক প্রথা।অভাবের সময় টাকা বা ধান ধার নিলে, মানে যে সময় চাষের কাজ অর্থাৎ রোয়া বা ঝাড়া থাকে না, সে সময় মজুরির হার কম থাকত, চাষের সময় বাড়ত। কিন্তু যখন ধার নেওয়া হল সেই রেটেই উচ্চ মূল্যের সময় কাজ করতে বাধ্য থাকতেন খেতমজুরটি। শ্রমের অভাবী বিক্রি আর কি! বামেদের অন্দোলন, খেতমজুরির দাম বেঁধে দেওয়া এক্ষেত্রে সুফল আনে। পরে অবস্থা এমন দাঁড়ায়, আগে খেতমজুররা খাতির করত বাবুদের, পরে বাবুদের তোয়াজ শুরু হয়, কাল কাজে যাস বাবা, যেন কামাই করিস না, বলে। ১৯৭৮ এর পঞ্চায়েত নির্বাচনে একটা প্রচার দলহীন গণতন্ত্রী এবং প্রচার মাধ্যম করেছিল: ‘ছোটলোকদের মাথায় তোলা’ বলে। তখন গ্রামে আর কটা কাগজ যেত, পড়ত-ই বা কজন, বাবুরা তো পড়ালেখা জানতেন। যাঁরা শোরগোল তোলেন, জ্যোতিবাবুর আমলে গোল্লায় গেছে বলে তাঁরা তাঁদের প্রচার সংখ্যার বৃদ্ধির মূলে যে বামফ্রন্টের তথাকথিত ‘ছোটলোকদের মাথায় তোলাটা’ দায়ী ---এটা আজ মানবেন কী?১৪বাজারি কাগজ অশোক মিত্রদের ওভারড্রাফট নিয়ে যত চেঁচামেচি করেছে তার এক শতাংশও যদি ইতিবাচক কাজগুলো নিয়ে করতো। কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্ক পুনর্বিন্যাস বা রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতার দাবিকে সমর্থন করতো তাহলে দেশের ইতিহাস-ই যেত বদলে। প্রচন্ড আর্থিক চাপের মধ্যেও বেকার ভাতা দেওয়ার কাজ কিন্তু বামফ্রন্ট-ই প্রথম করে। মাসে ৫০ টাকা, মানে বছর ৬০০ টাকা। আবার বলছি আজ ৫০ টাকা কিছু মনে না হলেও ১৯৭৭-এ ৫০ টাকায় ৬০ কেজি চাল বা ১০ কুইন্টাল আলু (হ্যাঁ, ১০ কুইন্টাল , আলু তোলার সময় কিনলে), বা তিন কুন্টাল বেগুন হতে পারতো। এই সময়ে বাজার দর একটু মনে করিয়ে দেওয়া যাক। এই প্রতিবেদক দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ার সময় থেকে হাট বাজারে যেত। তাই দাম মনে আছে।• নুন ১ কেজি – ৮ পয়সা • ডিম প্রতিটি - ৮ পয়সা• চাল ১ কেজি – ৬০/৮০/১০০ পয়সা• চিনি ১ কেজি -- ২ টাকা ৪০ পয়সা• জনতা শাড়ি ১ টি – ১৩ টাকা • সরষের তেল ১ কেজি -- ২টাকা ৪০ পয়সা • পোস্ত ১ কেজি – ৬ টাকা ( পোস্ত-র দাম ছিল বেশি)• রুই মাছ -- ২.৫০ টাকা থেকে ৪ টাকা• পুঁটি/ চিংড়ি/ চুনো মাছ ---৪০ পয়সা সের• বাঁধাকপি/ ফুলকপি – ১০-১৫ পয়সা পিস• কচু ১ কেজি – ১৫ পয়সা • মুরগির মাংস ১ কেজি -২০ টাকা• খাসির মাংস ১ কেজি ১০ টাকা• আলু যখন উঠতো ২০ পয়সা পাল্লাতেও পাওয়া যেত। মানে ৪ পয়সা কেজি। ১৯৮০তে আলু আশিন মাসে ৩৫ পয়সা কেজি হওয়ায় হাহাকার পড়ে গিয়েছিল।আমি এই দর লিখছি আমার জন্মস্থান রায়না থানা এলাকার পলাশন হাটের। আর ১৯৮২ তে পেঁয়াজ ৪ টাকা কেজি হওয়ায় কংগ্রেস দেওয়াল লিখেছিল – পেঁয়াজ আপেল একদরজ্যোতি প্রমোদ মাতব্বরকলকাতায় বাস ভাড়া ছিল ১০ পয়সা আর ২০ পয়সা।বেকার ভাতার ৫০ টাকার মূল্য কি বোঝা যাচ্ছে? তবে মাসে মাসে সবসময় মিলতো না। বছরে একসঙ্গে ৬০০ টাকা পাওয়া যেত। আমাদের গ্রামে যারা প্রথমে বেকার ভাতা পান তাঁরা কেউ বামপন্থী ছিলেন না।১৫এই প্রসঙ্গে বলতে হবে আরেকটি কথা। কর্মসংস্থান প্রকল্পের কথা। কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্র মারফৎ ঋণ পাওয়া যেত। একটু আগে দেখেছেন, মুরগির দাম ২০ টাকা কেজি, মানে খাসির মাংসের ডবল। মুসলিম পরিবারের মহিলারা কেবল মুরগি চাশ করতেন। তাও বহু বাড়িতেই এ নিয়ে অশান্তি হতো স্বামী-স্ত্রী র। মুরগি শাক সবজি-র খেত নষ্ট করে। ঘরের খড়ের চাল আঁচড়ায়। ঘর নোংরা করে ।মুরগি আর মুরগির ডিম বেচা পয়সায় মেয়েরা নিজের সঞ্চয়ের কাজে লাগাতেন। মুরগি খুব কম মিলত। তাই দামছিল চড়া। কর্মসংস্থান প্রকল্পের টাকায় বহু বেকার যুবক পোল্ট্রি চালু করেন। তাই মুরগির মাং খাওয়া সহজ হয়। খাসির দামের থেকে সস্তা হয়। মুরগির মাংস খাওয়ার সময় ৩৪ বছরের কিচ্ছু না করার ্কথা একটু মনে রাখবেন, অনুগ্রহ পূর্বক।এই যে ঋণ তাতে জ্যোতি বসু-অশোক মিত্রদের সরকার প্রথম ২০ শতাংশ ভর্তুকি দেওয়া চালু করে।শুধু ব্যাংক মারফৎ ঋণ দেওয়া নয়, ছাগল গরু মোষ শুয়োর হাঁস মুরগি, সেলাই মেশিন ও দিয়েছে বামফ্রন্ট সরকার। এমন এমনি গ্রামে আনন্দিত জলসা বসে না টিভি-র নামে। গ্রামে পয়সা এসেছে। তাই টিভি কিনতে পেরেছে প্রায় সব মানুষ। প্রসঙ্গত গ্রাম পিছু ১৯৭৭ এর আগে ৪ থেকে ৬ টির বেশি রেডিও ছিল না। টিভি দেখেই চোখে মানুষ।১৬ক্ষুদ্র চাষীদের ঋণে ভর্তুকি দান প্রথম বামফ্রন্ট সরকারের আরেকটি মহৎ অবদান। ব্যাংক ঋণ থেকে মুক্তির কথা তো শুরুতেই বলেছি। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিরা যাতে চাষ করতে পারেন তার জন্য মিনিকিট ধানের বীজ দেওয়া হতো। আজ যে মিনিকিটের এত রমরমা এবং অন্য চালের তুলনায় দাম কম—সেটা ও গাল দেওয়ার সময় মনে রাখবেন। আর দেওয়া হতো আলু, তিল সর্ষে, গমের বীজ—বিনা মূল্যে গরিবদের। আমলাতান্ত্রিক কারণে কখনো সেটা দেরিতে পৌঁছাতো—সে নিয়ে আক্ষেপও শুনেছি। ১৭বিধবা ভাতাদের দেওয়া প্রথম শুরু করে বাম সরকার। আমার এই সাল তা সঠিক মনে নেই। মাসে ৬০ টাকা। অনেকে উচ্চারণ করতে না পেরে বলতেন, পেন্সিল। বিভূতিভূষণের স্বপ্নের গোপালদের কাছে আসতেন বিধবারা , ‘ও বাবা গোপাল আমায় পেন্সিল দিবি নি’ বলে। কোন সাহিত্যিকের রচনায় এ সব প্রসঙ্গ তেমন দেখিনি।আর যাঁরা আমাদের রোদে জলে ভিজে বাঁচিয়ে রাখেন, যাঁদের ছাড়া টিভি কাগজ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় সব জায়গার বুকনি অচল, সমাজ ব্যবস্থা স্তব্ধ, সেই গফুর দের কারখানায় চলে যাওয়া বন্ধ করে, অনাহারে মরার হাত থেকে রক্ষা করে, যাঁরা মস্ত বড় সামাজিক দায়িত্ব পালন করেছিলে, কৃষকদের ভাতা প্রদান করে --তাঁদের কথা ভুলে যাওয়া মস্ত বড় সামাজিক অপরাধ।এ কথা যেন আমৃত্যু মনে রাখতে পারি।(ঋণ: #মার্কস_মোদি_মমতা বই )
ভাট...
 r2h | হ্যাঁ। কিন্তু এঁদের সবার নাকি জামিনই বাজেয়াপ্ত হয়েছে। মানুষ কী ভেবে কী হিসেবে ভোট দেয়, সেটা খুবই ঘোরালো। আমার দিল্লিতে গৌতম গম্ভীরের কাছে আতিশি মার্লেনার হেরে যাওয়াটা যেমন অতি আশ্চর্য লাগে। একজন রাজনীতিবিদ যে অনেকগুলি মিউনিসিপলিটি স্কুলের ভোল বদলে দেখিয়ে দিয়েছিলেন অল্প সময়ের মধ্যে, তিনি একজন ক্রিকেটারের কাছে হেরে গেলেন... অতি জটিল ব্যাপার।
r2h | হ্যাঁ। কিন্তু এঁদের সবার নাকি জামিনই বাজেয়াপ্ত হয়েছে। মানুষ কী ভেবে কী হিসেবে ভোট দেয়, সেটা খুবই ঘোরালো। আমার দিল্লিতে গৌতম গম্ভীরের কাছে আতিশি মার্লেনার হেরে যাওয়াটা যেমন অতি আশ্চর্য লাগে। একজন রাজনীতিবিদ যে অনেকগুলি মিউনিসিপলিটি স্কুলের ভোল বদলে দেখিয়ে দিয়েছিলেন অল্প সময়ের মধ্যে, তিনি একজন ক্রিকেটারের কাছে হেরে গেলেন... অতি জটিল ব্যাপার।  aranya | ভোট মানে তো লেসার ইভিল বেছে নেওয়া, সব দেশেই। ভারত ও পঃ বঙ্গের ক্ষেত্রে বাম দল গুলিকেই least evil , best option মনে হয় । ভোটার রা অবশ্য সেভাবে ভাবছে না। এখনও পর্যন্ত
aranya | ভোট মানে তো লেসার ইভিল বেছে নেওয়া, সব দেশেই। ভারত ও পঃ বঙ্গের ক্ষেত্রে বাম দল গুলিকেই least evil , best option মনে হয় । ভোটার রা অবশ্য সেভাবে ভাবছে না। এখনও পর্যন্ত aranya | আচ্ছা। দীপ্সিতা, সৃজন ইঃ রা জিতলে খুবই খুশী হতাম। হয়ত ভবিষ্যতে কখনো ..
aranya | আচ্ছা। দীপ্সিতা, সৃজন ইঃ রা জিতলে খুবই খুশী হতাম। হয়ত ভবিষ্যতে কখনো ..
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালতোমার বাস কোথা যে...-৫ - Nirmalya Nag
০৬ জুন ২০২৪ | ৪৬ বার পঠিতডাক্তারের চেম্বারের দরজা ঠেলে ঢুকে বিনীতা দেখল ব্যাগ গোছাচ্ছে ইন্দ্রনীল। বিনীতাকে দেখে একটু অবাক হল সে। “কিছু বলবেন, ম্যাডাম?” “আপনি বললেন প্রতিটা দিনই ইমপরট্যান্ট। ওর কন্ডিশন ঠিক কতটা খারাপ?” “আরে না না। শুনুন, এই কন্ডিশন থেকে লোকে সুস্থ হয়েছে এমন অনেক এক্সাম্পল আছে।” “তার মানে কন্ডিশন খারাপ। কতটা? ও কি–” বিনীতার কথা থামিয়ে দিল ইন্দ্রনীল। “শুনুন, যা যা করার সব করা হবে। বললাম না প্রথমে সার্জারি, তারপর–” এবার ইন্দ্রনীলকে থামাল বিনীতা। “ও সব আপনি আগেই বলেছেন। এখন ক্লিয়ারলি বলুন, ও কি টার্মিনাল পেশেন্ট?” “দেখুন ম্যাডাম…” “আমি যথেষ্ট স্ট্রং, আপনি বলুন।” ইন্দ্রনীল চুপ করে থাকে।
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজামাইক্রোপ্লাস্টিক ও মানবশরীর - স্বাতী রায়
০৫ জুন ২০২৪ | ৮৪ বার পঠিতশত্রুর নাম হল প্লাস্টিক। এমনিতে প্রচণ্ড দরকারি জিনিস। কিসে না লাগে! কিন্তু সমস্যা এইটাই যে প্লাস্টিক বলতে আমরা যে বিভিন্ন ধরণের রাসায়নিক দ্রব্য বুঝি, তাদের সবকটিকে পুনর্ব্যবহারযোগ্য করার কোন পকেটসই সুবিধাজনক পরিবেশ বান্ধব উপায় মেলে না। আবার সেটা এমনি ফেলে রাখলে প্রকৃতিতে মিশে যেতে অতি দীর্ঘ সময় লাগে। আর ততদিনে ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে সেটা ম্যাক্রো-প্লাস্টিক মেসো-প্লাস্টিক, মাইক্রো-প্লাস্টিক ইত্যাদি বিভিন্ন আকারের চেহারা নেয়। ম্যাক্রোপ্লাস্টিক হল ২.৫ সেমির থেকেও দৈর্ঘে বা প্রস্থে বড় যে কোন প্লাস্টিকের টুকরো। ৫ মিমি – ২.৫ সেমি অবধি টুকরোকে বলে মেসো-প্লাস্টিক। আর মাইক্রোপ্লাস্টিক বলা হও ১ মাইক্রো মিলিমিটার থেকে ৫ মিলিমিটারের সাইজের প্লাস্টিকের কণা। এই মাইক্রোপ্লাস্টিক নিয়েই আজকের কথা। কারণ আজকের দিনে এরা জলে স্থলে বাতাসে সর্বত্র ভেসে বেড়াচ্ছে।
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাভ্রমণের বিষ - প্রতিভা সরকার
০৫ জুন ২০২৪ | ১৫৮ বার পঠিতআমি বিদ্যাকে শুধোই, শুধু পাহাড়ের কি কোনো একক দেবতা নেই, যিনি তাকে রক্ষা করতে পারেন লাগাতার ধ্বংস আর নির্বিচার আক্রমণ থেকে? তাকে বলি, সমস্ত পাহাড়ের রাণী যে হিমাচল প্রদেশ তার চেহারা দিনের দিনের পর দিন যেভাবে কুৎসিত হয়ে উঠছে, তা কল্পনাতীত। পাঞ্জাব পেরিয়ে হিমাচলের সীমানায় ঢুকলেই শুধু উন্নয়ন, নির্মাণ, জেসিপি আর ট্রাকের পর ট্রাক! ট্যুরিজম পয়সা আনে, এজন্য রাস্তার পর রাস্তা তৈরি হচ্ছে, সিঙ্গল লেন ডাবল হচ্ছে বিয়াসের পাশে, সবচেয়ে উঁচু পাহাড়ের মাথায় পৌঁছে যাচ্ছে জেসিপি। ধুলোভরা গাড়ি চলার রাস্তাই হয়ত খুব শিগগিরই উন্নয়নের একমাত্র প্রতীক হয়ে উঠবে।
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাপরিবেশ ভাবনায় ভারতীয় সংস্কৃতি সাহিত্য: সেকাল-একাল - সন্তোষ সেন
০৫ জুন ২০২৪ | ২০১ বার পঠিতপরিবেশ বিপর্যয় আজ রাষ্ট্রীয় সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্ব চরাচরে পরিব্যাপ্ত। পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বেড়ে ১.৪৪ ডিগ্রির ঘরে, কোন প্রান্তে তীব্র দাবদাহ- খরা-তাপপ্রবাহ; অন্যত্র প্রবল বৃষ্টি-বন্যা-ধস, এমনকি দুটো বিপরীত এক্সট্রিম আবহাওয়া প্রায় একই সময়ে একই স্থানে আছড়ে পড়ছে। হিমবাহের অতিদ্রুত গলন, জল বাতাস নদীর দূষণ জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে প্রবলভাবে। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে সংবিধান-গণতন্ত্র-পরিবেশের সংকট সব জড়াজড়ি করে জট পাকিয়ে তুলেছে। প্রবল মূল্যবৃদ্ধি, বেকারি, আর্থিক বৈষম্য সহ পরিবেশ সংকটের মূল কারণ দেশি-বিদেশি বহুজাতিক কোম্পানির নির্বিচারে জল জঙ্গল জমি পাহাড় নদী: প্রকৃতির সব উত্তরাধিকার লুটেপুটে ধ্বংস করা।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালশিক্ষা নয়, ভিক্ষা - সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায়
০৫ জুন ২০২৪ | ৮৫৬ বার পঠিতকাল থেকে দেখি তথাকথিত বাম-সমর্থকরা ভর্তি করে লিখে চলেছেন, "শিক্ষা নয় জিতল ভিক্ষা"। আশ্চর্য হইনি, কারণ সিপিএমের মিছিলে গুচ্ছের লোক হয়, কিন্তু ভোট পায় বিজেপি। এঁদের সঙ্গে বস্তুত শাইনিং চাড্ডিদের বিশেষ তফাত নেই। রাজনীতি-ফিতি কিচ্ছু না, এঁদের মূলত দুটো দাবী। এক, বাম প্রার্থীরা খুব শিক্ষিত। দুই, পশ্চিমবঙ্গে হাইফাই চাকরি নেই, তাই বেঙ্গালুরুতে (কিংবা টিম্বাকটুতে) গিয়ে করেকম্মে খেতে হয়। শিক্ষিতরা খুব উঁচুদরের লোক, বাদবাকি ফালতু, এটা তাঁদের মাথার মধ্যে গেঁথে আছে, আর শিক্ষিতদের চাই মোটা-মাইনের চাকরি, এইটাকে তাঁরা প্রকৃত কর্মসংস্থান ভাবেন। দুটোই খুব সত্যি হতেই পারে (নাও পারে)। কিন্তু সেটা সমস্যা নয়, সমস্যা হল, এই দুটোই, বামপন্থা ছাড়ুন, যেকোনো মধ্যপন্থী জনপ্রিয় রাজনৈতিক চিন্তারই ঠিক উল্টোদিকে। মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্তদের কর্মসংস্থানের জন্য বিশ্বের প্রায় কোনো জনপ্রিয় নীতিই নির্ধারণ হয়না, হলেও মুখে বলা হয়না। খেটে-খাওয়া-মজদুর ইত্যাদিদের কথা অন্তত কাগজে-কলমে লেখা থাকে, কারণ বুক-বাজিয়ে "আমরা এলিট" বলার মতো দুঃসাহস নেহাৎই আত্মহত্যাপ্রবণ না হলে কোনো রাজনৈতিক দলই দেখায়না।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালযে যেখানে দাঁড়িয়ে - প্রবুদ্ধ বাগচী
০৩ জুন ২০২৪ | ১৬৮ বার পঠিতl লোকসভা ভোটের সম্ভাব্য ফলের রাজনৈতিক বিশ্লেষণ
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালদোলজ্যোৎস্নায় শুশুনিয়ায় - ১৬ - সমরেশ মুখার্জী
০৩ জুন ২০২৪ | ৫১ বার পঠিতআশির দশকে যাদবপুরের কয়েকটি ছাত্রছাত্রী শুশুনিয়া পাহাড়ে গেছে শৈলারোহণ অভ্যাস করতে - সেই ভিত্তিতে এই আখ্যান … বেশ লাগছে সুমনের। যেন ডিসেম্বরে বেসিক কোর্সে যা শিখেছে তারই একটা রিফ্রেশার্স কোর্স হচ্ছে
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালবুথফেরত ভূত - সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায়
০২ জুন ২০২৪ | ১৩৫৯ বার পঠিতবুথফেরত সমীক্ষা দেখে আপনি কি ভেঙে পড়েছেন? তাহলে শুনুন, চ্যানেলে চ্যানেল গতকাল যে সব পরিসংখ্যান পেশ করা হয়েছে তার বেশিরভাগ-ই ঢপের চপ। তেলে জল নয়, জলেই দুফোঁটা তেল। একেই পরিশীলিত ইংরিজিতে বলে স্ট্যাটিস্টিকাল মার্ভেল। উদাহরণ? কত চান? ১। রাজস্থান। News24 পূর্বাভাস দিয়েছিল যে রাজস্থানে বিজেপি ৩৩টি আসন জিতবে। জিততেই পারে, অঙ্কের হিসেব যখন। কিন্তু সমস্যা একটাই। রাজস্থানে আছেই মোট ২৫টি আসন। ২। হিমাচল। হিমাচলে Zee News এনডিএকে ৬-৮টি আসন দিয়েছিল। সেটাও অসম্ভব কিছু না, চারদিকে মোদি তরঙ্গ। কিন্তু সেখানেও সমস্যা একটাই। সেখানে আছে মাত্র ৪টি লোকসভা আসন আছে।
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাএক্সিট পোল - রমিত চট্টোপাধ্যায়
০২ জুন ২০২৪ | ৫৯৯ বার পঠিতআসুন দেখে নিই এক্সিট পোলের ভিতরের রহস্য
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজালেজ, বেড়াল, তপস্বী এবং ভণ্ড - বেবী সাউ
০২ জুন ২০২৪ | ৫৫৭ বার পঠিত হরিদাস পাল
হরিদাস পালবর্তমানে বাঁচা - সমরেশ মুখার্জী
০২ জুন ২০২৪ | ১৮৭ বার পঠিত৬০২ শব্দের এই খাজা ভাবনাটি লিপিবদ্ধ করেছিলাম ডিজিটাল ডায়েরিতে - চার বছর আগে - ১৮.০২.২১ - মনিপালে থাকতে। আজ ভাটের পাতায় চোখ বুলোতে গিয়ে kk - &/ - dc লিখিত তিনটি মন্তব্যে চোখ পড়লো। তার মধ্যে কেকের মন্তব্যের শেষটা বেশ বিমূর্ত - কিছু অনুক্ত অনুভবের আভাসমাত্র রয়েছে তাতে। ঐ তিনটি ভাট মন্তব্যের অনুরণন হিসেবে হপার পাতায় থাকলো অতীতের ডিজিটাল ডায়েরির পাতাটি
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালআমরা কি মাঙ্গলিক? - Mani Sankar Biswas
০২ জুন ২০২৪ | ১২৩ বার পঠিতপৃথিবীতে প্রাণ কী মঙ্গল গ্রহ থেকে এসেছে?
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাবিপ্লবের আগুন - পর্ব সাত - কিশোর ঘোষাল
০১ জুন ২০২৪ | ১০৩ বার পঠিতপরের দিন খুব ভোরবেলাতেই ভল্লার ঘুম ভেঙে গেল। আজ বেশ সুস্থ বোধ করছে সে। শরীরের ব্যথা, বেদনা – গ্লানি নেই বললেই চলে। বিছানায় উঠে বসল, তারপর ধীরে ধীরে ঘরের বাইরে এল। ভোরের আলো সবে ফুটেছে, বাইরের গাছপালার ডালে ডালে পাখিদের ব্যস্ততা টের পাওয়া যাচ্ছে তাদের কলকাকলিতে। হাওয়ায় সামান্য শিরশিরে ভাব। বিছানায় ফিরে গিয়ে সে গায়ের চাদরটা তুলে নিয়ে গায়ে জড়াল। দড়ি থেকে টেনে নিল গামছাটা – কষে বেঁধে নিল মাথায়। তারপর...
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালস্মৃতির রাজ্য শুধুই শ্লোগানময়-২ - প্রবুদ্ধ বাগচী
০১ জুন ২০২৪ | ১০৭ বার পঠিতবিগত চার দশকের রাজনৈতিক স্লোগান ও দেওয়াললিখন
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজারাবণের প্রার্থনা - তাতিন
০১ জুন ২০২৪ | ২৫৫ বার পঠিত... কোথায় গেল আজ সূর্যতিলক আর কোথায় ফার বনে মরেছে কাক নবমীমিছিলের অস্ত্র ঝনঝনে পকেটে গেল না কি পনেরো লাখ?...
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালভোটুৎসবে ভাট - হযপচো - সমরেশ মুখার্জী
০১ জুন ২০২৪ | ১৯০ বার পঠিতহঠাৎ কোনো প্রসঙ্গে মাথা চুলকে ওঠে। তা নিয়ে রম্যরচনা জাতীয় কিছু লিখে ফেলি। তবে সেসব রসে রম্য বা আঙ্গিকে রচনা পদবাচ্য হয় কিনা জানিনা। ভার্চুয়াল ডায়েরিতে দেখি এই ডিজিটাল ডায়েরিয়াটি লিখেছিলাম আজ থেকে ঠিক চার বছর আগে - ১লা জুন ২০২০. তখন ছিলাম মনিপাল, কর্ণাটকে। তবে এটার মূল প্রতিপাদ্য আজও রিলেভ্যান্ট। ভবিষ্যতেও থাকবে
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাকাদামাটির হাফলাইফ - ইট পাথরের জীবন - ইমানুল হক
০১ জুন ২০২৪ | ২৮৬ বার পঠিতআর কয়েকটা পরিবর্তন হয়েছে। ফুটবল খেলার মাঠে লোক নেই। সেখানে কিছুটা ঘিরে ঈদগাহ তলা। বেনে পাড়া বামুনপাড়ায় খেলার জায়গা ছিল না। দুটি পরিবার হাওড়া প্রবাসী হওয়ায় জায়গা মেলে। ছোটখাটো খেলার মাঠ হতেই পারতো। সেখানে এখন বড় দুর্গামন্দির। শিবমন্দির ছিল আগে মাটির। এখন শিব আর ওলাইচণ্ডীর আলাদা ঘর হয়েছে। আগে দুর্গাও ওখানে আসতেন। শিব লিঙ্গ সারা বছর থাকে। ওলাইচণ্ডীর বিসর্জন হয়। দুর্গারও। তবু আলাদা দুটি মন্দির।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালবৈঠকি আড্ডায় ১৭ - হীরেন সিংহরায়
০১ জুন ২০২৪ | ৫০০ বার পঠিতসকাল থেকে অন্ধকার হয়ে আছে আকাশ। কে বলবে এটা মে মাস ? বুথের ভেতরে ছ জন কর্মী , হলে আমরা চারজন । শুধু ভোটার কম পড়িয়াছে ! অনেকদিন আগে দেশে দেখা একটা ছবি মনে পড়ে গেল – আই এস জোহরের একটা কলাম ছিল ফিল্ম ফেয়ারে , তাতে কার্টুন :ফার্স্ট ক্লাস কামরায় একজন যাত্রী বসে আছেন তাঁকে ঘিরে কন্ডাক্টর , চা ওলা সহ আরও কয়েকজন । নিচে মন্তব্য - উই অলওয়েজ হ্যাভ মোর পিপল সারভিং ওয়ান কাসটমার !সারা দেশের ভোট গণনা শেষ হতে সকাল। প্রিসাইডিঙ অফিসার একেক বার মাইক দখল করে ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড ফলাফল ঘোষণা করেন । দশটি আসনের ন’টিতে লিব ডেম বিজয়ী। সবচেয়ে বড়ো সাফল্য- বারো বছরের সিটিং কাউন্সিলর ন্যাপহিলের পোস্ট মাষ্টার সাজ হুসেনকে হারালেন স্থানীয় রাজনীতিতে সম্পূর্ণ নতুন চেহারা জন পিয়ারস । তিনি ও আমি একত্রে জন গণেশের দুয়ার প্রদক্ষিণ করেছি কিন্তু ভাবতে পারি নি ষাট পেরুনো এক রিটায়ার্ড আই টি এঞ্জিনিয়ার সমাজে পরিচিত মুখ এক পোস্ট মাষ্টারকে দুশো ভোটের ব্যবধানে তাঁর আসন থেকে সরাতে পারবেন ! বোধহয় লেবার প্রধান মন্ত্রী হ্যারলড উইলসন বলেছিলেন, এ উইক ইজ এ লং টাইম ইন পলিটিক্স।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালভিকারুন্নেসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ! - Muhammad Sadequzzaman Sharif
০১ জুন ২০২৪ | ১৫৫ বার পঠিতমাউশির আইন আর ভিকারুন্নেসার আইন আলাদা! মাউশি যে বয়স সীমা দিয়েছে তার সাথে ভিকারুন্নেসার বয়স সীমার পার্থক্য আছে! এইটা অনেক অনেক অভিভাবকই জানে না। কেউ জানলেও মাউশি যেহেতু আবেদন করতে দিয়েছে দেখি আবেদন করে। আইনে না হলে বাতিল হয়েই যাবে, সমস্যা কী? সমস্যা হল ভিকারুন্নেসা তাদের আলাদা বয়স সীমা মাউশিকে জানায় নাই, নিজেরাও কোন উদ্যোগ নেয় নাই। ফলাফল? ১৬৯ জন শিশুর সুযোগ হয়ে গেছে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির! এরপরেও যদি দুই পক্ষ এইটার সমাধানের চেষ্টা করত তবুও বছরের মাঝে এসে এমন বিপদ তৈরি হত না এই ফুলের মতো শিশু গুলোর। লটারিতে টিকলেই তো হল না, বাচ্চার কাগজ পত্র সব ঠিক আছে কি না এগুলা যাচাই বাছাইয়ের ব্যাপার আছে না? ভিকারুন্নেসা এই যাচাই বাছাইয়ের কাজও সফল ভাবে করেছে। তখনও বাদ দেয় নাই এদেরকে! তখন বাদ দিলে এই অভিভাবকেরা একটু ঘাইঘুই করে মেনে নিত হয়ত। ভিকারুন্নেসা যুক্তি দেখাতে পারত যে আমাদের এখানে এই বয়স সীমা, এর বাহিরে আমরা নিব না। কিন্তু তা হয়নি। এদেরকে ভর্তি করা হয়েছে। বাচ্চারা ক্লাসও শুরু করেছে। ভিকারুন্নেসা তখন কেন এইটা করতে পারে নাই? তখন মহামান্য মাউশি ধমক দিয়ে বলেছিল তাদের আইনই আইন, এর বাহিরে কেউ আলাদা করে ভর্তির জন্য নতুন আইন তৈরি করতে পারবে না। আমার বন্ধু নিজে মাউশিতে গিয়েছিল, ওকেও মৌখিক ভাবে বলে দেয় যে সোজা ভর্তি করায় ফেলেন, আমরা যা বলছি ওইটাই ঠিক!
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালএক ‘নিউ বাংলাদেশ’ এর কথা - মোহাম্মদ কাজী মামুন
০১ জুন ২০২৪ | ১৯৯ বার পঠিতখবরে প্রকাশ, রাজধানী ঢাকার সৌন্দর্য পরিবর্ধনে বেশ কিছু প্রকল্প হাতে নিয়েছে ঢাকা দক্ষিন সিটি কর্পোরেশান। এর মধ্যে একটি প্রজেক্ট ১৯১৯ কোটি টাকার। যার আওতায় রয়েছে খেলার মাঠ, কমিউনিটি সেন্টার, পুকুর আধুনিকায়নের পরিকল্পনা, যার বাস্তবায়ন দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। এছাড়া কালুনগর, জিরানি, মান্দা ও শ্যামপুরে খাল নির্মাণেও অনুষ্ঠিত হচ্ছে ব্যাপক কর্মযজ্ঞ; সীমানপ্রাচীর, যানবাহন ও পথচারী চলার জন্য সেতু, পায়ে চলার পথ, পাবলিক টয়লেট, প্লাজা, সাইকেল লেন, আর বৈদ্যুতিক বাতির থাম – সব কিছু দাঁড়িয়ে যাচ্ছে ছায়াছবির মত। একই সাথে অনেক কিছু উধাও হচ্ছেও ছায়াছবির মত; যেমনঃ পুকুর বা খালের উন্নয়নে টনকে টন কংক্রিট গেলে দেয়া হচ্ছে পার্শ্ববর্তী সব সবুজকে উচ্ছেদ করে!
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজা'মোদী কি গ্যারান্টি': বিজ্ঞাপনতন্ত্রের এক নয়া রাজনৈতিক প্রয়োগ - অত্রি ভট্টাচার্য
৩১ মে ২০২৪ | ৩৬২ বার পঠিত'নিও-লেফট' বামপন্থার তাত্ত্বিক রেমন্ড উইলিয়ামস, তার বহুপঠিত 'অ্যাডভার্টাইজিং: দ্য ম্যাজিক সিস্টেম' নিবন্ধে দেখিয়েছিলেন, কিভাবে সমাজপরিমন্ডলের ব্যক্তিমানুষ পুঁজিতন্ত্রের দৌলতে 'বিষয়' হয়ে ওঠে, হয়ে ওঠে 'নির্বাচক'মাত্র এবং স্বয়ম্ভূ 'জনতা'র সার্বভৌম অবস্থান থেকে সে হয়ে ওঠে 'জনমত' নামক একরৈখিক, সমসত্ত্ব কন্ঠস্বর। সিদ্ধান্ত গ্রহণ গণতন্ত্রের একটি ফাংশনে' পর্যবসিত হয়, কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রণোদনা জোগানোর জন্য একটি নতুন ব্যবস্থা কায়েম করা হয়, যাতে করে সংখ্যাগরিষ্ঠকে একটি বিশেষ শাসনকাঠামো নির্মাণের লক্ষ্যে সংগঠিত করা যায়, তৈরি করে নেওয়া যায় নিজেদের প্রয়োজনীয় 'জনমত'। এই ব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠকে জনপিন্ড হিসাবে দেখা হয়, যাদের মতামত, জনসমূহ হিসাবে গৃহীত হবে, ব্যক্তি হিসাবে নয়, এই রূপান্তর 'বিজনেস অফ গভর্নেন্সের' একটি জরুরী ফ্যাক্টর। ব্যবহারিক পরিপ্রেক্ষিতে, এই রাজনীতি, বৃহৎ-পুঁজি, আমলাতন্ত্র ও বিজ্ঞাপনীজগতের মিলিঝুলি জাদুকাঠামো দীর্ঘ সময়ের জন্য সফলও হতে পারে, কিন্তু সামাজিক সমস্যাগুলি বর্ণনা করা ক্রমশ কঠিন হয়ে ওঠে, যেহেতু প্রচারকের পেশা এবং প্রচারকের বাস্তবতার ব্যবধান রয়েছে। অধিকন্তু, শাসক একটি অত্যাধুনিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় প্রকৃত ক্ষমতার জন্য ক্রমবর্ধমানভাবে আগ্রাসী ভূমিকা নেওয়ার ফলে, পুরানো সামাজিক-রাজনৈতিক প্রশ্নগুলি অপ্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে এবং, নয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণ সমস্ত সামাজিক কার্যকলাপের মূল উদ্দেশ্য হয়ে ওঠে।
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাবাংলায় বামের ভোট কি বাড়বে? - উপল মুখোপাধ্যায়
৩১ মে ২০২৪ | ৬০৫ বার পঠিতমন চায় বামের ভোট বাড়ুক। কিন্তু নরেন্দ্র মোদির ভারতে সম্ভবনার শিল্পে কি সে লেভেল প্লেয়িং গ্রাউন্ড আছে যেখানে বামেরা খেলতে পারে ? স্বতন্ত্র শক্তি হিসেবে বামেদের ভূমিকা এমনকি এই বাইপোলার পরিস্থিতিতেও অনস্বীকার্য। তাই তাদের ভোট দেওয়াটাও গুরুত্বপূর্ণ। খেলার ছলে কেই বা নেবে কৃষক আন্দোলনের অন্যতম চালিকা শক্তি বামেদের? মুশকিল হল ২০২৪ য়ের সাধারণ নির্বাচনে বামেদের বড় অংশকে বেশির ভাগ আসনেই ইন্ডিয়া জোটের আঁতাতের বাইরে প্রার্থী দিতে দেখা গেছে। সবচেয়ে বড় বাম দল সি পি আই এম দিয়েছে মোট বাহান্নটা আসনে। তার মধ্যে কেরালার পনেরোটা সিটে আর বাংলার তেইশটা যথাক্রমে কংগ্রেস আর তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। ইন্ডিয়া জোটের নেতৃত্ব এই শরিকি লড়াইয়ে ভাবিত নয় কারণ এই দু রাজ্যে জোট করতে যাওয়ার বাস্তবতা নেই। উল্টে করতে গেলে বিরোধী স্পেস বিজেপি খেয়ে নিতে পারে। এ কথাটা কেরালা আর পশ্চিম বাংলা এই দু রাজ্যে শুধু নয় পাঞ্জাবের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সেখানেও রাজ্যে ক্ষমতায় থাকা আপ আর কংগ্রেসের মধ্যে দা কাটারি সম্পর্ক। অর্থাৎ যেখানে নির্বাচনী জোট হয়নি সেখানে নির্বাচন পরবর্তী জোটের কথাই ইন্ডিয়া জোটের নেতৃত্বের মাথায় আছে। সে কথা মাথায় রেখে, পশ্চিম বঙ্গে দুই যুযুধান ইন্ডিয়া শরিক তৃণমূল কংগ্রেস আর বামফ্রন্ট-কংগ্রেস ভোট পরবর্তী অবস্থান নিয়ে এখনই বিতর্কে মেতেছে। উদ্দেশ্য নিজের নিজের ভোট ব্যাংক চাঙ্গা রাখা।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালদোলজ্যোৎস্নায় শুশুনিয়ায় - ১৫ - সমরেশ মুখার্জী
৩১ মে ২০২৪ | ৬১ বার পঠিতআশির দশকে যাদবপুরের কয়েকটি ছাত্রছাত্রী শুশুনিয়া পাহাড়ে গেছে শৈলারোহণ অভ্যাস করতে - সেই ভিত্তিতে এই আখ্যান … অমিয়দা বললেন, "কী বলতে চাইছি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো। ক্লাইম্বিং জগতে ওনারা মহাপুরুষ। নমস্য ব্যতিক্রম। অনেকেই পাহাড়ে দূর্ঘটনায় অকালে প্রয়াত। আমরা সাধারণ মানুষ। তাই চলবো সুরক্ষা নিয়ম মেনে। কী মনে থাকবে, তো?" শৈলারোহণ যে মোটেও ছেলেখেলার বিষয় নয় তা অমিয়দা দুটো বাস্তব উদাহরণ দিয়ে প্রাঞ্জল ভাবে বুঝিয়ে দিলেন …
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালকিষেণজি মৃত্যু রহস্য - পর্ব ১১ - বিতনু চট্টোপাধ্যায়
৩১ মে ২০২৪ | ১৩৩ বার পঠিতসেদিন ছিল ২০০২ সালের ২৬ অক্টোবর। একদম সকাল সকাল একটা খুন হল জামবনির জামুই গ্রামে। দিবাকর মালাকার নামে এক স্থানীয় সিপিআইএম নেতা তাঁর দুই সঙ্গী মানিক শতপথী এবং হেনা শতপথীর সঙ্গে মোটরসাইকেলে চেপে যাচ্ছিলেন। সকাল সাতটা-সাড়ে সাতটা হবে। দিবাকর মালাকার ছিলেন বাসু ভকতের অনুগামী এবং এলাকায় যথেষ্ট প্রভাবশালী নেতা। অত সকালে আক্রমণ হতে পারে ভাবতে পারেননি। খুব কাছ থেকে দিবাকর মালাকারকে গুলি করা হয়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হল দিবাকর মালাকারের।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালভোটুৎসবে ভাট - মক্ষী দর্পণ - সমরেশ মুখার্জী
৩০ মে ২০২৪ | ১০০ বার পঠিতশিরোনাম দেখে মনে হতে পারে লেখাটি “নীল দর্পণ” দ্বারা অনুপ্রাণিত। কিন্তু মক্ষী দর্পণে কোনো জ্বলন্ত আর্থসামাজিক বিষয়ে আলোচনা করা হয়নি। সে যোগ্যতাও আমার নেই। এটা ভোটের বাজারের হুল্লোড়ে পরিবেশিত একটি পাতি রম্যরচনা। এই ডিসক্লেমার সত্ত্বেও যদি কেউ লেখাটি পড়েন এবং বিরক্তির উদ্রেক হয় অনুগ্ৰহ করে আমায় গাল দেবেন না
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালসত্যজিৎ এবং কিশোরকুমার - সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায়
৩০ মে ২০২৪ | ১৬২ বার পঠিতসত্যজিৎ ঘরে-বাইরেতে সন্দীপের গলায় কিশোরকুমারকে গিয়ে গান গাইয়েছিলেন। কেন গাইয়েছিলেন? আপনারা সক্কলেই ঘরে-বাইরে পড়েছেন। ফলে আলাদা করে বলার কিছু নেই, রবীন্দ্রনাথের দুখানা উপন্যাস খুবই প্রচারধর্মী, গোরা এবং ঘরে-বাইরে। গোরাতে প্রায় চোঙা ফুঁকে ভালো-ভালো কথা বলা হয়েছে। ঘরে-বাইরেতে অতটা নয়। কিন্তু তাতেও, সেটা প্রায় কুরুক্ষেত্র। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং নিখিলেশ হয়ে সন্দীপকে শৈল্পিক কথার মারপ্যাঁচে নানা ব্রহ্মাস্ত্র ঝেড়েছেন। বিমলা বেচারি সেই যুদ্ধক্ষেত্রে প্রায় উলুখাগড়া। তাকে বাদ দিলে ওটা আর উপন্যাস না হয়ে 'স্বদেশী বিষয়ক আবর্তক ও নিবর্তক সম্বাদ' হয়ে যেত, তাই রাখা।
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাআইটির ভাইটি - কণিষ্ক
৩০ মে ২০২৪ | ১০৬৪ বার পঠিতআজকের যুগে দাঁড়িয়ে যেখানে তরুণ থেকে বয়স্ক সবাই নিয়মিত ইন্টারনেটে আনাগোনায় স্বচ্ছন্দ সেখানে নিজেদের সম্ভাব্য ভোটারকে টার্গেট করতে সমস্ত রাজনৈতিক দলই নিজেদের আইটি সেল তৈরি করে ফেলেছে। কারও আইটি সেল বেশি সক্রিয়, কারও কম, তবে প্রত্যেকেই অঞ্চল বুঝে, অডিয়েন্স বুঝে, কোন মাধ্যমে বলা হচ্ছে তার ওপর ভিত্তি করে ভিন্ন ভিন্ন ধরণের প্রচার কৌশল নিয়ে থাকে। কিন্তু কোনো কোনো রাজনৈতিক দলের আইটি সেল অনেক আগেই তাদের কার্যকলাপ শুরু করায় সেই পরিমাণ সাফল্য পেতে বা ততটা নেটওয়ার্ক তৈরি করতে বাকিদের আরোও বেশি কাঠখড় পোড়াতে হবে।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালমহাকাশের আলো - অনির্বাণ কুণ্ডু
৩০ মে ২০২৪ | ৩১১ বার পঠিত১৯৪৮ সালে র্যালফ আলফার ও রবার্ট হারম্যান দেখালেন, যে, গ্যামোর তত্ত্ব যদি সত্যি হয়, তাহলে সেই মহাবিস্ফোরণের কিছু অনুরণন এখনো খুঁজে পাওয়া উচিত। শক্তি বা তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গের ক্ষেত্রে এই অনুরণনটা হবে কৃষ্ণবস্তু বিকিরণ, যার উষ্ণতাও তাঁরা হিসেব করলেন, মান বেরোলো ৫ কেলভিনের মতন। ৫ কেলভিন মানে ‘–২৬৮° সেলসিয়াস’, অর্থাৎ মহাকাশ খুবই ঠান্ডা জায়গা। কিন্তু মহাবিশ্ব বরাবর এমন ঠান্ডা ছিল না। বিগ ব্যাং তত্ত্ব বলে, অতীতে মহাবিশ্বের আয়তন যখন খুব ছোটো ছিল, তখনো এই অনুরণনটা কৃষ্ণবস্তু বিকিরণই ছিল, কিন্তু তার তরঙ্গদৈর্ঘ্য ছিল অনেক কম, অর্থাৎ এক একটা ফোটনের শক্তি ছিল অনেক বেশি। যত দিন গেছে, এই বিকিরণ ঠান্ডা হয়ে এসেছে। অর্থাৎ, এই বিকিরণ খুঁজে পাওয়া গেলে আর উষ্ণতা হিসেবের সঙ্গে মিলে গেলে তা ‘বিগ ব্যাং’ তত্ত্বের পক্ষে অকাট্য প্রমাণ হবে।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালতোমার বাস কোথা যে... - ৪ - Nirmalya Nag
৩০ মে ২০২৪ | ২৮৬ বার পঠিত“অরুণাভ দাস। আপনাদের তো দেখেছি, গত মাসে মিস্টার শর্মার ছেলের বার্থডে পার্টিতে। গেছিলেন না?” পরিস্কার বাংলায় বলল ডাক্তার। “হ্যাঁ, কিন্তু…,” অরুণাভর কথা শেষ হল না, ইন্দ্রনীল হাত তুলে তাকে থামাল। “আপনার শার্ট, টাই আর স্যুট ছিল ডিফরেন্ট শেডস অফ ব্লু। আর ম্যাডাম,” বিনীতার দিকে তাকাল সে, “আপনি পরেছিলেন একটা লাল গর্জাস শাড়ি।” “বাব্বা, আপনি তো দারুণ লোক। গত মাসে পার্টিতে একবার দেখলেন, আর তাদের ড্রেস, শাড়ি সব মনে করে রাখলেন,” বলল অরুণাভ। “শুধু শাড়ি না, আরো অনেক কিছু বলতে পারি।” “মানে?” ভ্রূ কুঁচকে গেল বিনীতার।
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাপশ্চিমবঙ্গ - ফলাফল কী হতে চলেছে - সঞ্জয় সরকার
২৯ মে ২০২৪ | ৭০৩ বার পঠিতলোকসভা ভোট শেষ দফায়। এবার ভোটে উত্তুঙ্গ কোনো উদ্দীপনা ছিলনা, ছিলনা কোনো হাওয়া, চাপা এক উৎকণ্ঠা নিয়ে ভোট হয়েছে। সেই ধারা শেষ দফায়ও অব্যাহত। রাজনৈতিক পটচিত্রে উত্তেজনার অবশ্য কোনো অভাব হয়নি। অভাব হয়নি নাটকীয়তার। ভোটের ঠিক আগে নির্বাচনী বন্ড সংক্রান্ত রায় এসেছে সুপ্রিম কোর্টের। নির্বাচনের মধ্যেই এসেছে কলকাতা হাইকোর্টের পরপর দুটি রায়। একটিতে বিপুল সংখ্যক রাজ্য সরকারি শিক্ষককে কর্মচ্যুত করা হয়েছে, অন্যটিতে ২০১০ সালের পর পশ্চাদপদ অংশের সংরক্ষণকে একরকম করে বাতিল করা হয়েছে। দুটির চূড়ান্ত রায়ই অবশ্য সুপ্রিম কোর্টে ঝুলে। সন্দেশখালি ভোটের আগে থেকেই শিরোনামে। কিন্তু ভোটের মধ্যে এসেছে নতুন চমক। গঙ্গাধর কয়ালের এবং আরও কয়েকটি ভিডিও ফাঁস হয়ে ভাইরাল। এসেছে স্বয়ং রাজ্যপালের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থার অভিযোগ।
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাপায়েল কাপাডিয়ার ছবি, ভালোবাসা, বন্ধুত্ব ও রাজনীতি - সোমনাথ গুহ
২৯ মে ২০২৪ | ৩৩৯ বার পঠিতপায়েল কাপাডিয়ার ছবিতেও এই রাজনৈতিক সচেতনতার আভাস পাওয়া যায়। তাঁর ছবির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল রাজনীতি আর ব্যক্তিগত জীবন সমান্তরাল ভাবে চলে, এমনও মনে হতে পারে যেন দুটো ভিন্ন কাহিনি। রাজনীতি বলতে দলীয় মিটিং, মিছিল নয়, কোন ইস্যু, বিক্ষোভ, প্রতিবাদকে পূর্বনির্ধারিত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখা নয়, নির্মোহ ভাবে বৃহত্তর ও ব্যক্তিগত পরিসর কে ফুটিয়ে তোলা। পায়েল আগেও কান উৎসবে অংশগ্রহণ করেছেন, পুরষ্কার জিতেছেন। ২০১৭ সালে তাঁর ‘আফটারনুন ক্লাউডস’ একমাত্র ভারতীয় ছবি যা উৎসবে নির্বাচিত হয়েছিল। ২০২১ সালে তাঁর তথ্যচিত্র ‘আ নাইট অফ নোইং নাথিং’ সেরা ডকুমেন্টারি ছবির জন্য ‘গোল্ডেন আই’ পুরষ্কার পায়। এই ছবিতে ২০১৫ সালে FTII এ মহাভারত-খ্যাত গজেন্দ্র চৌহানকে প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ করার প্রতিবাদে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল তা দেখান হয়েছে। প্রসঙ্গত পরিচালক নিজে এই আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন যার জন্য তিনি প্রায় সাড়ে চার মাস ক্লাস বয়কট করেছিলেন এবং তাঁর অনুদানও বন্ধ হয়ে গেছিল। ছাত্রদের এই প্রতিবাদ দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছড়িয়ে পড়ে। এরই মধ্যে এক কলেজের ছাত্রী তার প্রেমিকের অনুপস্থিতি অনুভব করছে। একই চিঠিতে সে লিখছে ক্যাম্পাসে কী হচ্ছে সে বুঝে উঠতে পারছে না, হয়তো স্ট্রাইক করার জন্য তাঁদের শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। মুসলিম যুবককে চোখ বেঁধে, কোমরে পিস্তল ঠেকিয়ে পুলিশের জিপে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, একই সাথে মেয়েটি চিঠিতে তার চারিপাশের বাস্তব, কল্পনা, স্বপ্ন, ফ্যান্টাসি উজাড় করে দিচ্ছে। এই ভাবে পরিচালক পলিটিকাল আর পারসোনালের মধ্যে আন্তসম্পর্ক খুঁজছেন, বোঝার চেষ্টা করছেন।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালদোলজ্যোৎস্নায় শুশুনিয়ায় - ১৪ - সমরেশ মুখার্জী
২৯ মে ২০২৪ | ৯৬ বার পঠিতআশির দশকে যাদবপুরের কয়েকটি ছাত্রছাত্রী শুশুনিয়া পাহাড়ে গেছে শৈলারোহণ অভ্যাস করতে - সেই ভিত্তিতে এই আখ্যান … অমিয়দা বললেন, "আমি তোমাদের রক ক্লাইম্বিং কোর্সে যাইনি। তাই এখন সরাসরি পাথরে গিয়ে চড়ার আগে শৈলারোহণের যে কিছু নিয়মকানুন আছে, যা তোমরা কোর্সে শিখেছো সেগুলো একটু ঝালিয়ে নেওয়া যাক। তোমরা হয়তো জানো শৈলারোহণ ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল ইওরোপে, বলা ভালো মূলতঃ ব্রিটেনে। তাই এখোনো বহু দেশে ব্রিটিশ মাউন্টেনিয়ারিং কাউন্সিল বা BMC প্রবর্তিত ক্লাইম্বিং টেকনিক, প্রোটোকল, সুরক্ষা নিয়ম, ইকুইপমেন্ট স্পেসিফিকেশন ইত্যাদি গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে বিবেচিত হয়। তার কারণ ব্রিটিশরা খুব মেথডিক্যাল।" …
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজানরেন্দ্র মোদীর গুজরাট মডেল - দ্বিতীয় পর্ব - প্রদীপ দত্ত
২৮ মে ২০২৪ | ৯৩২ বার পঠিতসেন্টার ফর মনিটরিং ইন্ডিয়ান ইকোনমির (সিএমআইই) তথ্য দেখায় যে, ২০০৩ সাল থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত, গুজরাটে এই ধরনের বিনিয়োগকারী সম্মেলনগুলিতে দেওয়া প্রতিশ্রুতির মাত্র ২৫ শতাংশ দিনের আলো দেখেছিল৷ অনেক বিজেপি শাসিত রাজ্য একে মডেল হিসাবে গ্রহণ করেছে। যেমন -- হ্যাপেনিং হরিয়ানা, মোমেন্টাম ঝাড়খণ্ড, রিসার্জেন্ট রাজস্থান ইত্যাদি। উত্তরপ্রদেশ (ইউপি ইনভেস্টর সামিট), পশ্চিমবঙ্গ (বেঙ্গল গ্লোবাল সামিট), ঝাড়খন্ড এবং ওড়িশাও বিনিয়োগের উপযুক্ত গন্তব্য হিসাবে নিজেকে তুলে ধরার জন্য ভাইব্রেন্ট গুজরাট সামিটের অনুরূপ সংস্করণ আয়োজন করেছে। কিন্তু সব জায়গাতেই একই কান্ড– বড় বড় ঘোষণার কিছুকাল পর দেখানোর মতো কিছু নেই। ইভেন্টের সময় যে মৌ (এমওইউ) স্বাক্ষরিত হয়, খুব কমই প্রকৃত বিনিয়োগ হয়, কারণ মৌগুলির কোনও আইনি বাধ্যবাধকতা নেই। এই জাতীয় শোগুলির পর বলার মতো কর্মসংস্থান যে হয় এমন কোনও বিশ্বাসযোগ্য তথ্যও নেই।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালভোটুৎসবে ভাট - স্বপনে তাহারে (পুনশ্চ) - সমরেশ মুখার্জী
২৮ মে ২০২৪ | ৯৮ বার পঠিতআগে মাঝেমধ্যে টুকটাক ঢুকলেও গুরুতে প্রথম মজলুম ২৮.১০.১৮ সন্ধ্যায়। সেদিন ২৪.৭.১৪তে শিবাংশু লিখিত “আমাকে তুই আনলি কেন…” চোখ পড়লো। খানিকটা পড়েই জমে গেলাম। অতঃপর অনেক রাত অবধি ২১ পর্বের ১১ হাজার শব্দেরও বেশী সেই লেখা একলপ্তে পড়ে শেষ করলাম। শুধু তাই নয়, মাঝে মাঝে থাকতে না পেরে, তার কিছু কিছু ভালো লাগা অংশ কপি করে হোয়াতে পেষ্ট করে মুষ্টিমেয় কজন বন্ধু এবং এক প্রাচীন বান্ধবীকেও পাঠিয়েছি। শিবাংশু গুরুতে (আপাতত) শেষ লেখাটি লেখেন ২০.৩.২১ - “স্বপনে তাহারে” - বিখ্যাত ডিডেকটিভ গল্প লেখক স্বপনকুমার প্রসঙ্গে। বর্তমান খাজা রচনাটি সেটি হতে অনুপ্রাণিত
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজানরেন্দ্র মোদীর গুজরাট মডেল - প্রথম পর্ব - প্রদীপ দত্ত
২৭ মে ২০২৪ | ১১৭৭ বার পঠিতগুজরাত দাঙ্গার সময় রাস্তায় উন্মত্ত হিন্দু গোষ্ঠীর লোকেরা শুধু স্থানীয় মুসলমানদেরই হত্যা করেনি, এক হাজারের বেশি ট্রাকও জ্বালিয়ে দিয়েছিল। জেনারেল মোটরস কারখানায় তৈরি জাহাজে পাঠানো ‘ওপেল অ্যাস্ট্রা’ গাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়ার খবর আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে হেডলাইন হয়েছিল। এক হিসাবে দেখা যায় দাঙ্গায় গুজরাটের দু’হাজার কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছিল। ওই সাম্প্রদায়িক হিংসা আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীদের ভীতিগ্রস্ত করে তোলে। শিল্পপতিদের ধারণা ছিল পরে গোলমাল আরও বাড়বে। সেই বছর সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে গুজরাতে ফরেন ডায়রেক্ট ইনভেস্টমেন্ট (এফডিআই) আসা একেবারে বন্ধ হয়ে যায়।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালদিলদার নগর - Aditi Dasgupta
২৭ মে ২০২৪ | ১৫৪ বার পঠিতঘরে এলে নাকি গেলে দেহলীটি ছুঁয়ে? নিশ্চিত না জানি। যেই পথে তুমি গেলে সাগরের ঢেউয়ে --- সেই পথে আমি তো উজানী !
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজামোবাইলে ‘না’ নির্বাচনে কমিশনের! - অর্ণব মণ্ডল
২৭ মে ২০২৪ | ৪৩১ বার পঠিতসম্ভবত, কোনও ভোটার যাতে পোলিং বুথে ঢুকে ছবি তুলতে বা ভিডিও করতে না পারেন, সেই জন্যই মোবাইল ফোন, ক্যামেরা বা এই ধরনের কোনও রকম বৈদ্যুতিন যন্ত্র নিয়ে বুথে প্রবেশের ওপরে এই নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। কিন্তু, ভিডিও বা ছবি তো নির্বাচনী স্বচ্ছতার জন্য আরও বেশি করে প্রাসঙ্গিক। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্থানে সংবাদ মাধ্যমের ক্যামেরায় বুথের অভ্যন্তরের বিভিন্ন অনৈতিক কার্যকলাপের দৃশ্য ধরা পড়েছে। পোলিং অফিসারদের হুমকি দিয়ে সম্মিলিত ভাবে বুথ জ্যাম, দেদার ছাপ্পা – এসব ঘটনা তো আমাদের কাছে অতিপরিচিত। তাই বুথের ভেতরে যদি কেউ বা কয়েকজন মিলে গণ্ডগোল পাকানোর চেষ্টা করে, ভোটারদের কাছে ফোন থাকলে সেটার ছবি তোলা বা ভিডিও করা যাবে তৎক্ষণাৎ, যেটা পরে প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করে অপরাধীদের ধরার ক্ষেত্রে সেগুলো কাজে লাগতে পারে। শুধু ইভিএম মেশিনে একজনের ভোটদানের দৃশ্য যাতে অন্য কেউ না তুলতে পারে, সে বিষয়ে কড়া নজর রাখতে হবে।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালচালচিত্র এখন - সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায়
২৭ মে ২০২৪ | ৮৯৪ বার পঠিতচালচিত্র এখন সিনেমাটাও এই রীতি অনুসরণ করেই বানানো। যদিও অত পুরোনো না, এবং অত গভীর অনুসন্ধানেরও প্রয়োজন পড়তনা, কিন্তু সেটুকুও করার দরকার মনে হয়নি। এই সিনেমায় আশির দশকের কলকাতায় দিব্যি ল্যাজ তুলে ঘুরে বেড়ায় নীল-হলুদ বেসরকারি বাস, আশিতে সেসব বাস কেউ চোখে দেখেনি। শব্দ শোনা গেলে তারা হয়তো নিউটাউন-নিউটাউন বলেও হাঁক পাড়ত। দেখা যায়, সবুজ অটো। নায়কের বৌয়ের নাম মাঝেমধ্যেই মিতা থেকে বদলে গীতা হয়ে যায়। এবং মিতা ওরফে গীতা মিনার্ভা থেকে উত্তরপাড়া যেতে নিয়মিত শিয়ালদহ স্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধরেন। শিয়ালদা থেকে উত্তরপাড়া ট্রেনে চড়ে যাওয়া একেবারে অসম্ভব কিছু না, কিন্তু সে তো নৈহাটি-ব্যান্ডেল হয়েও যাওয়া যায়, সাধারণভাবে সুস্থ লোকে ওই দিক দিয়ে নিয়মিত যায় না আর কি।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালতিন দশকের প্রাচীন টি - সমরেশ মুখার্জী
২৭ মে ২০২৪ | ২১৪ বার পঠিতব্যক্তির জীবনে তিনটি দশক বড় কম সময় নয়। এই দীর্ঘ সময়ে ঘরে বাইরে তার নিজস্ব পরিসরে অনেক কিছু বদলায়। পুরানো গাড়ি বাতিল হয়, নতুন গৃহে প্রবেশ হয়, পুরানো সম্পর্কে শ্যাওলা ধরে, নতুন অহং পুষ্ট হয়, পুরানো স্মৃতি ধূসর হয়, নতুন মানে খুঁজতে হয়। এমন নানা পরিবর্তনের প্রভাবে কখনো জীবনের কিছু সরল সমীকরণ ক্রমশ বিবর্তিত হয় জটিল অসমীকরণে। এসবের মাঝে তিন দশক ধরে একটি সামান্য টি-শার্ট কিভাবে এহেন সার্ভিস দিয়ে যায় ভেবে অবাক লাগে
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালমানুষ ঠকানোর গল্প! - Muhammad Sadequzzaman Sharif
২৭ মে ২০২৪ | ২১৮ বার পঠিতআমার খালার ফোনে ফোন আসল একটা। উনার বিকাশ ( বাংলাদেশের অন্যতম সেরা মোবাইল ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান) একাউন্টের পিন নাম্বারে সমস্যা হয়েছে, ঠিক করাতে হবে। খালার সাথে কথা বলে ওরা বুঝছে এই মহিলা এগুলা কম বুঝে। ওদের আত্মবিশ্বাস এতো যে তারা বলছে যে বুঝে তার কাছে নিয়ে যান। খালা আমার কাছে আসতেছিল পথে মধ্যে আরেক 'বিশেষ ভাবে অজ্ঞ' একজনের সাথে দেখা, তিনি তাদের সাথে কথা বলে যেমন যেমন করতে হয় তেমন তেমন করে কাজ সমাধা করেছেন। খালা এরপরে আসছে আমার কাছে। এসে বলল তোমার কাছেই আসতেছিলাম, বিকাশের পিন ঠিক করতে হব বলে, পথে অমুকের সাথে দেখা, ও ঠিক করে দিল! আমি শুনেই বুঝলাম এইটা গন কেস! বললাম, খালা বিকাশে টাকা কত ছিল? খালা বলল চার পাঁচ হাজারের মতো। আমি বললাম, ব্যালেন্স দেখেন, সম্ভবত এক টাকাও নাই! খালা বলে আরে না, ওরা তো পিন ঠিক করার জন্য বলছে। আমি বললাম, আপনে দেখেন! দেখা হল, ফিনিশ! এক টাকাও নাই!
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালদোলজ্যোৎস্নায় শুশুনিয়ায় - ১৩ - সমরেশ মুখার্জী
২৬ মে ২০২৪ | ২০৮ বার পঠিতআশির দশকে যাদবপুরের কয়েকটি ছাত্রছাত্রী শুশুনিয়া পাহাড়ে গেছে শৈলারোহণ অভ্যাস করতে - সেই ভিত্তিতে এই আখ্যান … ঈশু বলে, "দ্যাখ জেঠু, এই ক্যাম্পিংয়ে একমাত্র গৌরব ছাড়া আমরা আর কে কতটা রক ক্লাইম্বিং করতে পারবো জানি না তবে আজকের এই আলোচনাটা খুব এনজয় করলাম। অনেক কিছু জানলাম। এর আগে কোনোদিন এমন স্পর্শকাতর বিষয়ে এভাবে খোলামেলা আলোচনা কারুর সাথে হয়নি। তাই এই আউটিংটা বহুদিন মনে থাকবে। থ্যাঙ্কস জেঠু। তোকে প্রায়শঃই চ্যাংড়ামি করতে দেখে ভাবতাম তুই একটা লঘুচিত্ত, চপলমতির ছেলে। তুই যে এমন সব সংবেদনশীল বিষয়েও এতো সাবলীল ভাবে আলোচনা করতে পারিস, জানা ছিলো না। এবার চল আমরা শুতে যাই, অনেক রাত হয়েছে। কাল সকালে তাড়াতাড়ি উঠতে হবে।" তখনও সুমন জানতো না, আগামীকাল গভীর রাতে ওকেই আবার এই কথাটা বলতে হবে ঈশুকে, অন্য পরিস্থিতিতে
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাকাদামাটির হাফলাইফ - ইট পাথরের জীবন - ইমানুল হক
২৫ মে ২০২৪ | ২৯৯ বার পঠিতযে বাড়িতে সত্যপীরের পালা, সে বাড়ির ছেলে মেয়েরা লোকেদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলে আসতো। সত্যপীরের ভূমিকায় যিনি অভিনয় করতেন তাঁর হাতে থাকতো একটা বিরাট সাদা চামর। সেটা মাথায় বুলিয়ে তিনি আশির্বাদ করতেন। হিন্দু মুসলমান সবাই সেই আশির্বাদ নিতেন। ১০-২০ পয়সা করে দিতেন মায়েরা সত্যপীরের পালায়। কিশোর ঘোষালদা লিখেছেন, ১৯৮০ র মাঝামাঝি সত্যপীর সত্যনারায়ণ হয়ে গেল। তা, সত্যপীরের পালায় হিন্দু মুসলমান একতার কথা থাকতো।
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাসীমানা - ৪৮ - শেখরনাথ মুখোপাধ্যায়
২৫ মে ২০২৪ | ১৫১ বার পঠিতস্যর স্ট্র্যাফোর্ড আর দ্বিতীয়বার দেখা করেননি গান্ধীর সঙ্গে, করে লাভ ছিল না। তিনি অবিশ্যি সত্যি-সত্যিই ভারতের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন, সেরকমই পরিকল্পনা ছিল তাঁর, কিন্তু সেই পরিকল্পনার ধার ধারতেন না তাঁর বস, উইনস্টন চার্চিল। সেই সময়কার ভাইসরয় লিনলিদগোও চার্চিলেরই দলে। ক্রিপ্সের মতো অনেক সোশ্যালিস্ট দেখা আছে তাঁদের। হামবাগ সব! জওহরলাল আর সেই সময়কার কংগ্রেসের রাষ্ট্রপতি মৌলানা আজাদ অবিশ্যি ক্রিপসের সঙ্গে একমতই ছিলেন, ছিলেন এমনকি রাজাগোপালাচারিও, যদিও লীগের ব্যাপারে কংগ্রেসের অবস্থানের প্রতিবাদে কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন রাজাগোপালাচারি নিজে। এখন গান্ধী একাই বিরোধীপক্ষ, যদিও নিজে গান্ধী মনে করেন না তা। তিনি মনে করেন সমস্ত দেশবাসী তাঁর পক্ষে। তিনি একবার সঙ্কেত দিলেই প্রায় প্রতিটি ভারতবাসী নেমে পড়বে রাস্তায়, তাদের মুখে থাকবে একটাই কথা, ভারত-ছাড়! যদি নিজে থেকে না ছাড়, আমরাই ছাড়াব তোমাদের। করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে!
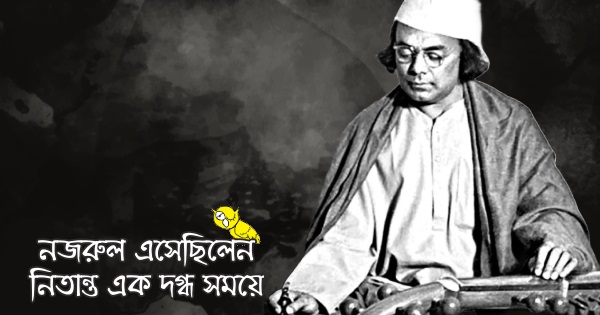 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজানজরুল এসেছিলেন নিতান্ত এক দগ্ধ সময়ে - সৈয়দ তৌশিফ আহমেদ
২৫ মে ২০২৪ | ৪২৪ বার পঠিতপ্রতিকূলতার মুখে দাঁড়িয়ে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবনা যেভাবে প্রত্যাঘাত করেছে, সেটাকেই নজরুল শব্দের স্বচ্ছন্দ গতিতে রূপান্তর ঘটিয়ে গেছেন বরাবর, কিছুটা একবগগা এবং ছেলেমানুষের মতই। গূঢ় দর্শন তাঁর লেখার বাঁধনহারা উচ্ছলতায় খাদ মেশায় নি কখনও, তেমনই পুনরাবৃত্তিও পিছু ছাড়েনি। নজরুল ঠিক এখানেই স্বেচ্ছাচারী অসংযমী অসচেতন, এবং তাঁর সৃষ্টির অনেকাংশই গভীর ভাবলোকে অনুত্তীর্ণ। তবে ওই ঐচ্ছিক খামতিগুলোই কি তাঁকে অনন্য করেনি? তিনি তো একাই হয়ে উঠেছেন একটা ঘরানার আদি ও অন্ত। পূর্ব ও উত্তরসূরি না থাকা এক অদ্বিতীয় ধারা। এমনই এক তেজস্ক্রিয়তা, অর্ধ জীবনকালের সূত্র মেনে যার ফুরিয়ে যাওয়াটা নির্ধারিত। সেই ফুরিয়ে যাওয়াতেও অবশ্য তাঁর মস্ত সাফল্য।
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাবিপ্লবের আগুন - পর্ব ছয় - কিশোর ঘোষাল
২৫ মে ২০২৪ | ৩৭৫ বার পঠিতশুকনো পাতা দিয়ে বানানো গদিতে ভল্লা শুয়ে আছে। আজ পাঁচদিন হল সে একইভাবে শুয়ে আছে, নিশ্চেতন। তার মাথার কাছে বসে আছেন জুজাকের বউ। জুজাক দাঁড়িয়ে আছেন পায়ের দিকে। আর নিচু হয়ে বৃদ্ধ কবিরাজ হাতের নাড়ি পরখ করছেন ভল্লার। কিছুক্ষণ পর কবিরাজ ভল্লার হাতটা নামিয়ে দিলেন, বিছানায়। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, “জুজাক, আমার মন বলছে, ছোকরা এ যাত্রায় বেঁচে গেল। হতভাগার বাপ-মায়ের কপাল ভালো বলতে হবে।”
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজামহারাজ ছনেন্দ্রনাথের নামরহস্য - রমিত চট্টোপাধ্যায়
২৫ মে ২০২৪ | ৪৬৬ বার পঠিতব্যস, এই সুযোগের অপেক্ষাতেই তো ছেনু ছিল, এক ছুটে দুধের গ্লাস হাতে তেতলার সিঁড়িতে উঠে পড়ল। এবার পা টিপে টিপে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে সিঁড়ি দিয়ে তেতলায় পৌঁছে ভালো করে তাকিয়ে দেখে নিলো কেউ আছে কিনা। যখন দেখতে পেল চারিদিক ফাঁকা, কেউ তার দিকে নজর রাখছে না, তখন গ্লাস থেকে এমন করে এক চুমুক দুধ খেলো, যাতে চলকে কিছুটা দুধ মুখ বেয়ে নেমে আসে, তারপর একটা বিচ্ছিরি মুখ করে কোনোক্রমে ঢোঁক গিলে সেই এক চুমুক দুধ গলা দিয়ে চালান করে নিচু হয়ে বসে ড্রেনের মুখটায় বাকি দুধটা আস্তে করে ঢালতে লাগল। ঢালতে ঢালতেও কড়া নজর চারদিকে, এই বুঝি কেউ দেখে ফেলল। ধীরে ধীরে পুরো দুধটাই ঢালা হয়ে গেলে আস্তে করে উঠে আবার সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এল।
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাস্লোভাকিয়া ৪ - হীরেন সিংহরায়
২৫ মে ২০২৪ | ২৬৪ বার পঠিতব্রাতিস্লাভায় সিটি ব্যাঙ্কের নবীন কর্মী মারেক পটোমা বলেছিল নিজের দেশ না হলে আইস হকিতে স্লোভাক প্লেয়ারদের জায়গা জুটবে না তাই আমরা আলাদা হয়েছি! দেশ ভাগের এর চেয়ে জোরালো যুক্তি আমি অন্তত খুঁজে পাই নি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে উইলসন ডকট্রিন মাফিক ইউরোপে স্বায়ত্ত শাসনের যে দাবি উঠেছিল তার ফলে পুরনো অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্যের অংশ বিশেষ মিলে তৈরি হলো চেকোস্লোভাকিয়া, এই মাত্তর ১৯১৮ সালে। ক্যাথলিক ধর্মের প্রাধান্য দুই অঞ্চলে, চেকের সঙ্গে স্লোভাক ভাষা প্রায় ৮৫% মেলে; আমার প্রাক্তন সহকর্মী ইভেতার (এখন আবু ধাবিতে) কাছে গল্প শুনেছি – অফিসে সে কিছু নিয়ে আলোচনা করছে এক চেক কলিগের সঙ্গে। আরেক স্থানীয় সহকর্মী জিজ্ঞেস করে, তোমরা কোন ভাষায় কথা বলছ? ইভেতা বলে, নিজের নিজের মতন, আমি স্লোভাক এবং উনি বলছেন চেক! আমাদের হিন্দি/উর্দু সংলাপের মতন।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালহাটুয়া সাধু ভোটুয়া ফকির - Naresh Jana
২৫ মে ২০২৪ | ৪০৩ বার পঠিতসাধু হন্টন
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালভোটুৎসবে ভাট - এত বুড়ো কোনোকালে হব নাকো আমি - সমরেশ মুখার্জী
২৫ মে ২০২৪ | ১৮৬ বার পঠিত৪২% প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে ৬৩ শীত পার করেও আমার লেখ্যভঙ্গিতে লঘু রম্যরসময়তার প্রবণতা গেল না। অথচ ঐ রস উচ্চমার্গীয় আঙ্গিকে পেশ করার যোগ্যতাও নেই। তাই ওসব ধ্রুপদী পাঠকের ঋদ্ধরুচির উপযোগী নয়। ফলে তাঁদের রুচিশীল মন্তব্যে শালীন বিশেষণে অল্পাধিক উষ্মা, বিরক্তির প্রকাশ হয়ে পড়ে - যেমন “ঘাসবিচালি টাইপ রসিকতা”। তাতে অবশ্য আমি বিশেষ বিচলিত হই না। বিড়ম্বিতবোধও করি না। বরং তা নিয়েও আবার “খেলো টাইপস” রসিকতা করে ফেলি - এই যেমন এখন করছি।
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাশ্রী শ্রী উনিজি কথামৃত - সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায় ও কণিষ্ক
২৪ মে ২০২৪ | ৩১২২ বার পঠিতপ্রকাশিত হলো দুই মলাটে বৈদ্যুতিন উনিজি কথামৃত। লিখেছেন সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায়, এঁকেছেন নবীন শিল্পী কণিষ্ক। শিল্পীর সম্পর্কে বেশি জানা যায়নি, তিনি রাতের অন্ধকারে মেলবক্সে ছবির বান্ডিল ফেলে দিয়ে গেছেন। জানিয়েছেন উনিজির প্রতি অনুগত থাকতে চাইলে মাথা বর্জন করা ভালো, আর অনুগত থাকতে না চাইলে গর্দান যাওয়ার সম্ভাবনা, সুতরাং আগে থেকে মুন্ডু বিসর্জন দেওয়াই বিধেয়। নামিয়ে নিন, ছড়িয়ে দিন - উনিজি কথামৃত - পিডিএফ সংস্করণ।
- আরও বুলবুলভাজা ... আরও হরিদাস পাল ...
-
গুরুচণ্ডা৯-র গ্রাহক হোন
কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে গুরুচণ্ডা৯-র গ্রাহক হোন। গুরুচণ্ডা৯তে প্রকাশিত লেখাগুলি পেতে চাইলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যুক্ত হোন, অথবা, আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলটির গ্রাহক হোন।
- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই
- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... kk, দ)
(লিখছেন... Prativa Sarker, kk, প্রতিভা)
(লিখছেন... অরিন, kk, সন্তোষ সেন )
(লিখছেন... Somnath Pal, রমিত চট্টোপাধ্যায়, পোল খুলে গেল)
(লিখছেন... Prabhas Sen, Argha Bagchi, সিক্যুয়েল চাই)
- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন
(লিখছেন... )
(লিখছেন... r2h, অরিন, Ruchira)
(লিখছেন... মোহাম্মদ কাজী মামুন, দ)
(লিখছেন... সমরেশ মুখার্জী)
(লিখছেন... এরাও তাই বলছে, Prativa Sarker, বিপ্লব রহমান)
- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... অরিন, অরিন, অমিতাভ চক্রবর্ত্তী)
(লিখছেন... সমরেশ মুখার্জী, ছোট মুখে , সমরেশ মুখার্জী)
(লিখছেন... পাপাঙ্গুল, দীপ, দীপ)
(লিখছেন... kk, দীপ, dc)
(লিখছেন... )
- কি, কেন, ইত্যাদি
- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...
- আমাদের কথা
- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...
- বুলবুলভাজা
- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...
- হরিদাস পালেরা
- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...
- টইপত্তর
- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...
- ভাটিয়া৯
- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...