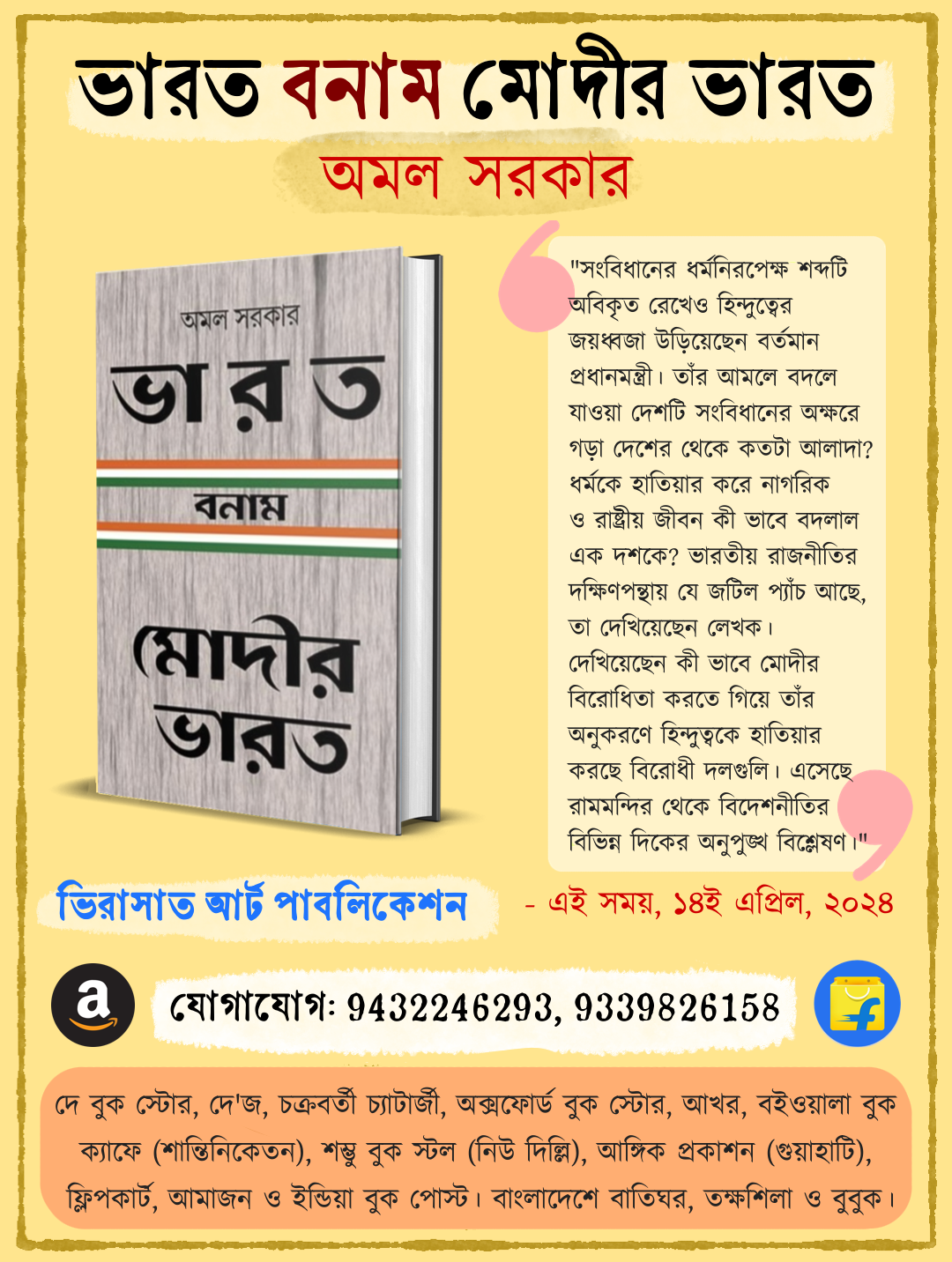- হরিদাস পাল ব্লগ

-
বাম-ভোটের ‘রাম’ হয়ে যাওয়ার গুজব – একটি পোস্ট-ট্রুথ প্রোপাগান্ডা
Debasis Bhattacharya লেখকের গ্রাহক হোন
ব্লগ | ১২ মে ২০২১ | ১০৪৯৭ বার পঠিত | রেটিং ৪.৭ (৩ জন) - পশ্চিমবঙ্গের সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনের পর রাজ্যের মসনদ ধর্মান্ধ হিংস্র মৌলবাদী শক্তির হাতে চলে যেতে পারে, এমন সম্ভাবনায় আতঙ্কিত ছিলেন এ রাজ্যের গণতন্ত্র-প্রিয় মানুষ। ফলপ্রকাশের পর যখন দেখা গেল যে তা ঘটেনি, তখন তাঁরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেও, উঠে এসেছে এক অস্বস্তিকর প্রশ্ন। এ রাজ্যের পূর্বতন ক্ষমতাসীন বাম শক্তি, বিশেষত তার বড় শরিক সিপিএম, কি মৌলবাদী শক্তিকে গোপনে সাহায্য করেছে? অর্থাৎ, তাদেরকে ক্ষমতা থেকে যারা হঠিয়েছে, সেই তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতি ক্রোধ ও প্রতিহিংসা বশত তাদের কর্মী ও সমর্থকেরা কি বিজেপি-কে ভোট দিয়ে ক্ষমতায় আনতে চেষ্টা করেছিলেন? নির্বাচনের আগে থেকেই এ হেন সম্ভাবনার কথা হাওয়ায় ভাসছিল কোনও কোনও মহলে, এবং নির্বাচনের পর তার ‘প্রমাণ’ মিলেছে বলে দাবি করছেন কেউ কেউ। যাঁরা এ আশঙ্কার কথা বলছেন, তাঁদের একাংশও নিজেদেরকে বামপন্থীই বলেন, এবং কেউ কেউ বিশুদ্ধতর বামপন্থী বলে দাবি করে থাকেন। প্রশ্ন হচ্ছে, নির্বাচনী ফলাফল থেকে সত্যিই এমন ইঙ্গিত মেলে কি? সেটাই আজ আমরা এখানে পর্যালোচনা করে দেখব।
গোপন ব্যালট ব্যবস্থায় কে কাকে ভোট দিয়েছে তা সরাসরি বোঝার উপায় নেই, কিন্তু ভোটের তথ্য খুঁটিয়ে লক্ষ করলে কিছু না কিছু মোদ্দা প্রবণতা তো বেরিয়ে আসেই। সে পথে হেঁটে কতদূর এগোতে পারা যায়, দেখা যাক।
এটা ঘটনা যে, সিপিএম-এর নির্বাচনী প্রচারে আক্রমণের বর্শামুখটা ততটা বিজেপির দিকে ছিল না, যতটা ছিল তৃণমূলের দিকে, বিশেষত তৃণমূলের বিরুদ্ধে ওঠা দুর্নীতির অভিযোগগুলোর দিকে। এ অবস্থান আকার পেতে সাহায্য করেছে উপরোক্ত অভিযোগটিকে। আর তার ওপর, ভোটের মোদ্দা ফলাফল পূর্ববর্তী বিধানসভা নির্বাচনের (২০১৬) সঙ্গে তুলনা করলে আপাতদৃষ্টিতে এমনটা মনে করার সুযোগ থাকছে যে, আশঙ্কাটি হয়ত বা সত্যিই হবে। তৃণমূল গতবারে ভোট পেয়েছিল ৪৫ শতাংশ, এবারে পেয়েছে ৪৮, অর্থাৎ এবারে গতবারের চেয়ে ৩ শতাংশ ভোট বেশি পেয়েছে। বিজেপি গতবারে ভোট পেয়েছিল ১০ শতাংশ, এবারে পেয়েছে ৩৮, অর্থাৎ এবারে গতবারের চেয়ে অভাবনীয় ২৮ শতাংশ বেশি পেয়েছে। সিপিএম-এর ভোট হয়েছে ২০ থেকে ৫ শতাংশ, অর্থাৎ তারা খুইয়েছে ১৫ শতাংশ। কংগ্রেস-এর ভোট হয়েছে ১২ থেকে ৩ শতাংশ, অর্থাৎ তারা খুইয়েছে ৯ শতাংশ (সবই পূর্ণসংখ্যায়, ভগ্নাংশ না ধরে, এক নজরে সবটা পেতে চিত্র-১ দেখুন)। ফলে, খুব সহজ যে চিন্তা প্রথমেই মাথায় আসবে সেটা এই যে, তৃণমূল তো ভোট হারায়নি বরং বাড়িয়েছে, তাহলে বিজেপির ভোটে এই অভাবনীয় বৃদ্ধি আর কোথা থেকে আসবে, বামেদের হারিয়ে ফেলা ভোট যদি ওখানে না ঢুকে থাকে? যাঁরা আগে থেকেই এমন আশঙ্কা করছিলেন, এ সহজ ব্যাখ্যা তাঁদের কাছে অনিবার্য বলেই মনে হবে। অনেকে তা থেকে এমনও অনুসিদ্ধান্ত টেনেছেন যে, তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ওঠা দুর্নীতি ও গুণ্ডাবাজির অভিযোগগুলোর কারণে ‘অ্যান্টি-ইনকাম্বেন্সি ফ্যাক্টর’ প্রবলভাবে কাজ করবে এবং তার ফলে ভোটারদের এক বড় অংশ তাদের প্রতি বিরূপ হবেন বলে যে প্রত্যাশা বিরোধী দলগুলো করেছিল, তেমনটা আদৌ ঘটেনি, অর্থাৎ তাদের বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ আদৌ জাগ্রত হয়নি। কিন্তু, ব্যাপারটা কি সত্যিই অতখানি সোজা? ভেবে দেখা যাক একটু।
মনে করুন যদি এমন হয় যে, তৃণমূলের বিরুদ্ধে আসলে ‘অ্যান্টি-ইনকাম্বেন্সিফ্যাক্টর’ ঠিকই কাজ করেছে, এবং তার দরুন তাদের নিজেদের ভোটের এক বড় অংশ বাস্তবিকই বিজেপির দিকে ঝুঁকেছে, কিন্তু সিপিএম-সহ অন্যান্য নানা পক্ষের ভোট আবার তৃণমূলের পক্ষে গিয়ে তাদের মসনদকে রক্ষা করেছে (বা অন্তত পাকা করেছে) --- তাহলেও তো মোদ্দা শতাংশের হিসেবটা একই দাঁড়াবার কথা, তাই না?
জানি, এ অনুমানে কোনও কোনও পাঠক বিরক্ত হবেন। বলবেন, ধুর মশায়, যে সহজ সরল সত্যিটা সাদা চোখেই বোঝা যাচ্ছে তাকে অস্বীকার করে একটা জটিল গল্প ফাঁদছেন কোন দুঃখে? এমন কি, তিনি যদি দর্শনচর্চা করেন, তো আমাকে মধ্যযুগীয় ব্রিটিশ যুক্তিশাস্ত্রী ওকাম সাহেবের নীতিবাক্যও মনে করিয়ে দিতে পারেন --- কোনও ঘটনা বা তথ্যকে যদি সরলভাবে ব্যাখ্যা করা যায়, তাহলে অকারণে জটিল ব্যাখ্যা আমদানি করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। কাজেই, আমাকে এখন খুলে বলতে হবে, জটিল ব্যাখ্যা ফাঁদছি কোন দুঃখে। সত্যি বলতে কী, সে দুঃখ একটা নয়, অন্তত গোটা তিনেক। প্রথমত, তৃণমূলের প্রতি যতই রাগ থাক, সিপিএম নিজের ভোট-ভাণ্ডারটি, যা নাকি ইতিমধ্যেই ক্ষীয়মান, তা বিজেপির হাতে তুলে দিয়ে নিজেকে পুরো মুছে দিতে চাইবে --- এমন অনুমান একেবারেই উদ্ভট ও অবান্তর। দ্বিতীয়ত, সিপিএম যে পনেরো শতাংশ ভোট হারিয়ে ফেলেছে তার পুরোটাও যদি বিজেপিতে গিয়ে থাকে (সাধারণ বুদ্ধিতে যা অসম্ভব), তাহলেও তা দিয়ে বিজেপির ২৮ শতাংশ ভোটবৃদ্ধির মাত্র অর্ধেকটা ব্যাখ্যা হয়, বাকি অর্ধেক অব্যাখ্যাতই থাকে। এমন কি, সিপিএম ও কংগ্রেসের মোট খুইয়ে ফেলা যে ভোট, অর্থাৎ ১৫+৯=২৪ শতাংশ, তার পুরোটা বিজেপিতে গেছে এইটা ধরে নিলে তার পরেও বাকি চার শতাংশ (২৮-২৪=৪) অব্যাখ্যাত থাকে। তৃতীয়ত, নির্বাচনের প্রাক্কালে দলে দলে বিজেপিতে যোগদান করা তৃণমূল নেতারা কোনও ভোটই সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারেন নি এ অনুমানও অসম্ভব, কারণ তা যদি হত, আর যাই হোক, নন্দীগ্রামে স্বয়ং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অন্তত হারতেন না। এত দুঃখের পরে সহজ সত্যি আর তত সহজ থাকবে না, বলা বাহুল্য।
তাহলে, নির্বাচনী বাস্তবতাকে খুঁজব কোন পথে? অবশ্যই সত্যান্বেষণের চিরকেলে পথে --- তথ্য, যুক্তি, বিশ্লেষণ। দেখতে হবে, গত দুটি বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল কী ইঙ্গিত দিচ্ছে। এ জন্য প্রথমেই আমরা তাকাব এবারে বিজেপি যে সাতাত্তরটি আসন জিতেছে তার ইতিহাসের দিকে, সে ইতিহাস এক নজরে পেতে হলে দেখুন চিত্র-২। এই আসনগুলো আগে কাদের দখলে ছিল সে তথ্য সবিস্তারে পাবেন এ চিত্র থেকে, বস্তুত এটি একটি সারণি।
এই সারণির তথ্যের পরিসংখ্যানগত সারাৎসার দিয়েছি তার পরের ছোট্ট এক লাইনের সারণিটিতেই, দেখুন চিত্র-৩। বিজেপি-বিজিত সাতাত্তরটি আসনের মধ্যে কতগুলো কোন দলের জিম্মায় ছিল তা এখানে পাবেন এক নজরেই, এবং পাশেই ব্র্যাকেটে পাবেন প্রত্যেকের আলাদা আলাদা শতাংশের হিসেব। ভাল করে দেখুন, এই সাতাত্তরের মধ্যে যেখানে তৃণমূল থেকে গেছে আটচল্লিশটি আসন (প্রায় বাষট্টি শতাংশ) এবং কংগ্রেস থেকে পনেরোটি (প্রায় কুড়ি শতাংশ), সেখানে সিপিএম থেকে গেছে মাত্র ছয়টি (প্রায় আট শতাংশ) এবং বাকি বামদলগুলোকে ধরলে সব মিলিয়ে প্রায় বারো শতাংশ। অর্থাৎ, এর মধ্যে প্রায় বিরাশি শতাংশ অবদানই যে অ-বাম দলের, সে নিয়ে বোধহয় আর কোনও কথাই হওয়া উচিত নয়।
আচ্ছা, এবার উল্টো দিক থেকে ব্যাপারটা দেখা যাক। গতবার সিপিএম যে ছাব্বিশটা আসন পেয়েছিল, এবারে সেগুলোরই বা কী গতি হল? সে তথ্য এক নজরে পাবার জন্য দেখুন চিত্র-৪,
এবং একইভাবে তার পরিসংখ্যানগত সারাৎসারের জন্য দেখুন চিত্র-৫। কী দেখলেন বলুন তো? ওর মধ্যে বিজেপিতে গেছে মাত্র ছটা (তেইশ শতাংশ), আর তৃণমূলে গেছে পুরো বাকিটাই, অর্থাৎ কুড়িটা (সাতাত্তর শতাংশ)! এখানেও বামভোটের রাম হওয়ার খুব বেশি ইঙ্গিত নেই, অন্তত ঘাসফুল হওয়ার থেকে বেশি ইঙ্গিত নেই, তাই না?
চিত্র-৬ থেকে পাওয়া যাচ্ছে ইতিপূর্বেই বিজেপির হস্তগত তিনটি আসনের পরিণতি সংক্রান্ত তথ্য। সংখ্যার স্বল্পতার কারণে এ থেকে টানা সিদ্ধান্ত খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ হবে না, কাজেই এ সারণিটি এখানে না দিলেও হয়ত খুব ক্ষতি হত না। তবু বলি, বিগত কয়েক বছরে অর্জিত বিজেপির নিজস্ব ভোট যে এবারে খুব বেশি স্থানচ্যুত হয়নি, তার একটা আবছা ইঙ্গিত এর মধ্যে আছে।
অবশ্য, এইসব হিসেব নিকেশের পরেও একটা আপত্তি তোলা যায়। বলা যায়, এক নির্বাচন থেকে আরেক নির্বাচনে কিছু না কিছু ভোট তো এক থেকে আরেক দলে গিয়েই থাকে, তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। সেখানে যে দলের ভোটের ভাঁড়ার বেশি তার থেকে নির্গমনের আয়তনও বেশি হবে, আর যে দলের ভাঁড়ারে মা ভবানী তার থেকে নির্গমনও কম হবে, এ তো জানা কথাই। কাজেই, শুধু এইটুকু দেখিয়ে এ কথা মোটেই প্রমাণ হবে না যে, সিপিএম থেকে কিছু বাড়াবাড়ি রকমের ভোট বিজেপিতে যায় নি। এ প্রশ্নের মীমাংসা করতে গেলে কয়েকটি অনুপাত হাজির করা প্রয়োজন। এখন পর্যন্ত ঘোষিত ২৯২ সংখ্যক আসনের মধ্যে বিজেপি পেয়েছে ৭৭, অর্থাৎ শতাংশের হিসেবে দাঁড়াচ্ছে মোটামুটি ২৬.৩৭ শতাংশ। এখন, এই সংখ্যাটার সঙ্গে কীসের তুলনা করব? তৃণমূল, কংগ্রেস ও সিপিএম থেকে বিজেপি যে আসনগুলো হাতাতে পেরেছে সেগুলো আনুপাতিক হিসেবে ওই মোদ্দা অনুপাতটার চেয়ে কম না বেশি --- এ তুলনা থেকে হয়ত কিছু মূল্যবান ইঙ্গিত মিললেও মিলতেও পারে। বিগত বিধানসভায় তৃণমূল পেয়েছিল ২১১-টি আসন, আর কংগ্রেস পেয়েছিল ৪৪-টি আসন, মানে মোট ২৫৫। এবারে তা থেকে বিজেপির কব্জায় গেছে মোট ৬৩-টি (৪৮+১৫), অর্থাৎ প্রায় ২৫ শতাংশ। দেখা যাচ্ছে, অনুপাতটা প্রায় একই, হয়ত বা এক-দেড় শতাংশ কম। সেখানে সিপিএম-এর পূর্বতন ২৬-টি আসনের মধ্যে ৬-টি গেছে বিজেপির কব্জায়, অর্থাৎ প্রায় তেইশ শতাংশ, মানে বিজেপির মোট আসনলাভের মোদ্দা অনুপাতের তুলনায় প্রায় সাড়ে তিন শতাংশ কম। অতএব আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারছি, সিপিএম থেকে বিজেপিতে যাওয়া ভোট যদি কিছু থেকে থাকে (কিছু তো আছেই), তো সেটা কোনও হিসেবেই তৃণমূলের চেয়ে বেশি নয়। ফলত, সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির শক্তিবৃদ্ধির প্রশ্নে তৃণমূলের দায়ও কোনওভাবেই সিপিএম-এর থেকে কম নয়।
এখানে অবশ্য একটা স্বীকারোক্তি করে রাখা উচিত হবে। এই যে আমি আসন দিয়ে ভোটের হিসেব কষছি, এটা কিন্তু পরোক্ষ হিসেব, এখানে একটু ফাঁক থেকে যেতে পারে। কমবেশি ভোটের সঙ্গে কমবেশি আসনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তো আছেই, কিন্তু সে সম্পর্ক মোটেই সব সময় সমানুপাতিক নয়। যদি এবারের ও গতবারের নির্বাচনে প্রতি আসনে বিভিন্ন দলের প্রাপ্ত ভোট-সংখ্যা দিয়ে সত্যিকারের ভোট হিসেব করা হত, এবং বঙ্গীয় নির্বাচনের এক দীর্ঘমেয়াদি প্রেক্ষাপটে ফেলে তাকে বিচার করা যেত, তাহলে নিশ্চয়ই আরও নির্ভরযোগ্য সিদ্ধান্তে আসা যেত, এবং আরও অনেক লুকোনো সত্যিই হয়ত বেরিয়ে আসতে পারত। তবে, এখানে যে মোটাদাগের চিত্রটা উঠে আসছে সেটা তাতে পুরোপুরি খারিজ হয়ে যেত, আমার তা মনে হয়না। আমার ধারণা, তাতে বরং এই চিত্রটিই আরও পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠবে।
তা সে যাই হোক, এখন দেখা যাক, এই ভোট-সংখ্যার খেলাটা আরেকটু খেললে আরও কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায় কিনা। ওপরে দেখেছি, সিপিএম ও কংগ্রেস মিলিয়ে এবারে মোট চব্বিশ শতাংশ ভোট খুইয়েছে। আর এই বড় চারটি দল বাদ দিয়ে অন্যান্যরা, যাদের মধ্যে মূলত আছে সিপিএম ছাড়া অন্যান্য বাম দল, মুসলমান ধর্মভিত্তিক দল, নিম্নবর্গীয় রাজনীতির দল --- এদের মোট ভোট তেরো থেকে কমে গিয়ে হয়েছে পাঁচ শতাংশ, অর্থাৎ এখানেও প্রায় আট শতাংশ ভোট খোয়া গেছে। মানে, সব মিলিয়ে বত্রিশ শতাংশ, খুব কম নয় মোটেই। স্পষ্টতই, এ ভোট ভাগ হয়েছে বিজেপি ও তৃণমূলে। ওপরের আলোচনায় এ ইঙ্গিত পাওয়া গেছে যে, এর বেশিটাই গেছে তৃণমূলে। কিন্তু ধরুন, তাকে পাত্তা না দিয়ে যদি একটা ‘নিরাপদ’ অনুমানে যাই, এবং ধরে নিই যে এর ভাগ তৃণমূল ও বিজেপি সমানভাবে পেয়েছে, তাতেও তৃণমূলের ভাগে দাঁড়ায় ষোলো শতাংশ। যদি তৃণমূল এবারের ভোটে নিজের ভোটব্যাঙ্ক একটুও না খোয়াত, তাহলে গতবারের পঁয়তাল্লিশ শতাংশের সঙ্গে এই বাড়তি ভোট জুড়ে তৃণমূলের ভোট গিয়ে দাঁড়াত একষট্টি শতাংশে, কিন্তু তার বদলে হয়েছে আটচল্লিশ শতাংশ, অর্থাৎ বাস্তবে তাদের ভোট বেড়েছে মাত্র তিন শতাংশ। কীভাবে সম্ভব, যদি তৃণমূলের পূর্বতন সমর্থকেরা দলে দলে শিবির পরিবর্তন না করে থাকেন?
তাহলে, এ সবের অর্থ তবে কী? ধর্মান্ধতা ও সাম্প্রদায়িক হিংসার প্রবল উন্মত্ত ঝড়ে, এবং কিঞ্চিৎ প্রতিষ্ঠানবিরোধী ক্ষোভের উত্তাপেও, বাম-অবাম সবারই বিস্তর ভোট মৌলবাদী রাজনীতির শিবিরে উড়ে গিয়ে পড়েছে --- এ অনুমান সহজসাধ্য। কিন্তু, বামেদের মধ্যেই যে অংশ এ ঝড়েও অবিচলিত ছিলেন (তাঁরাই যে বেশিরভাগ, সে ইঙ্গিত ওপরে আছে), তাঁরাই বা নিজেদের প্রার্থীকে বঞ্চিত করে খামোখা তৃণমূলকে ভোট দেবেন কেন, বিশেষত যখন তাঁদের পার্টির ভোট-প্রচারের বর্শামুখ ছিল তৃণমূলের দিকেই? সত্যি বলতে কী, এ ধাঁধার উত্তর বোধহয় সবচেয়ে ভাল দিতে পারবেন স্বয়ং বাম ভোটার এবং তাঁদের নেতারাই। তবুও, আমরা যে অন্তত যৌক্তিক সম্ভাবনাগুলোকে একটু নেড়েচেড়ে দেখতেও পারিনা, এমন তো আর নয়। কে জানে, হয়ত পূর্বতন বাম ভোটারদের কাছে বাম রাজনীতি আর তেমন প্রাসঙ্গিক নয়। কিংবা, বাম রাজনীতি প্রাসঙ্গিক হলেও, বর্তমান বাম দলগুলো আর প্রাসঙ্গিক নয়। কিংবা, দুইই প্রাসঙ্গিক, কিন্তু তাঁদের মনে হয়েছে, ধর্মান্ধ হিংস্র মৌলবাদী রাজনীতিকে আটকাতে নিজের ভোটটা এদিক ওদিক দিয়ে নষ্ট না করে তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীর শিবিরে জড়ো করা উচিত --- সেটাই এই মুহূর্তের কর্তব্য। কিংবা হয়ত, এই সবই একসাথে, কোনও এক জটিল রাসায়নিক অনুপাতে। কিংবা, আসলে হয়ত এর কোনওটিই নয়, এ হল পশ্চিমবঙ্গীয় ভোটারদের এক বৃহত্তর দীর্ঘমেয়াদি আচরণ-নকশার অঙ্গমাত্র। তাঁরা তিন দশক কংগ্রেসকে ক্ষমতায় রেখে হঠাৎ একদিন হুড়মুড়িয়ে ফেলে দিয়েছেন, সাড়ে তিন দশক বামফ্রন্টকে দেখে নিয়ে অকস্মাৎ ক্ষমতাচ্যুত করেছেন, এবং এখন হয়ত অপেক্ষা করছেন, আরও দুই-আড়াই দশক পরে হঠাৎ এক সুন্দর নির্বাচনী প্রভাতে তৃণমূল উৎপাটিত করবেন বলে।
বঙ্গের নির্বাচনী রথযাত্রার রথটিতে বিজেপি উঠতে পারেনি, কিন্তু শক্ত মুঠিতে হাতল চেপে ধরে ঝুলে পড়েছে। দিদি ভাবছেন আমি দেব, পিকে ভাবছেন আমি, ‘নো ভোট টু বিজেপি’ শিবিরের লোকজনও যে কিছুই ভাবছেন না এমন নয় (আমি স্বয়ং এই শেষোক্ত দলেই পড়ি)। ভোট-অন্তর্যামী মহোদয় অলক্ষ্যে হেসেছেন কিনা, সেটা হয়ত সমাজবিজ্ঞানীরা আমাদেরকে জানাতে পারবেন বেশ কয়েক বছর পরে।
পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় একান্তভাবে ব্যক্তিগত ক্যারিসমা-নির্ভর একটি পপুলিস্ট দল এবং মৌলবাদী দল ছাড়া আর অন্য কোনও দল না থাকা, এবং বামেদের পরিসর মুছে যাওয়া, সম্ভাব্য কোনও অর্থেই সুলক্ষণ নয়। রাজ্যের গণতান্ত্রিক ভবিষ্যৎ এবং আম জনতার জন্য তো নয়ই, এমন কি ‘বিশুদ্ধ’ বামেদের জন্যও নয়। মূলস্রোত বামেদের কাজ-কর্ম-চিন্তা যেমনই হয়ে থাকুক, রাজনৈতিক পরিসরে দীর্ঘদিন যাবৎ তাদের অস্তিত্ব এক ‘রেফারেন্স ফ্রেম’ হয়ে থেকেছে, যার সাপেক্ষে ‘বিশুদ্ধ’ বাম নিজের অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধতার দাবিটি ওঠাতে পারেন। এখন যদি রামচন্দ্রের অশেষ কৃপায় সে রেফারেন্স ফ্রেম ভেঙে চুরমার হয়ে যায়, ওই বিশুদ্ধতা তার যাবতীয় অর্থ ও প্রাসঙ্গিকতাটুকু হারাবে।
ঠিক কী কারণে কে কতটা ভোট পেল বা না পেল সে নিয়ে যত তর্কবিতর্কই হোক, দিনের শেষে তাহলে ঘটনা গিয়ে দাঁড়াচ্ছে এটাই যে, বাংলার মসনদে তৃণমূলের আসন পোক্ত হয়েছে, অযুক্তি অন্ধত্ব ধর্মান্ধতা হিংস্রতা বিদ্বেষের রাজনীতির শক্তিবৃদ্ধি হয়েছে ভীতিপ্রদ গতিতে, এবং বামেরা মুছে গেছেন নির্বাচনী পরিসর থেকে। সবচেয়ে খারাপ যেটা ঘটতে পারত সেটা ঘটেনি, কিন্তু বিরাট কিছু স্বস্তির কারণও ঘটেনি। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে ক্ষমতা দখল থেকে বহুদূরে বিজেপিকে আটকে রাখা গিয়েছে, কিন্তু আসলে তৃণমূলের সঙ্গে তাদের ভোটের পার্থক্য মাত্রই দশ শতাংশ, এবং আর মাত্র তিন-চার শতাংশ ভোট ইধার-উধার হলেই খেলাটা পুরো ঘুরে যাবে। পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান ভোটার যদি কম করে পঁচিশ শতাংশও ধরি, এবং যদি ধরে নিই যে তাঁরা বিজেপিকে মোটেই ভোট দেন নি, তো তার অর্থটি দাঁড়াবে সাংঘাতিক --- বাকি পঁচাত্তর শতাংশের মধ্যে আটত্রিশ শতাংশ --- মানে সংখ্যাগুরু হিন্দু ভোটের অর্ধেকের বেশিই বিজেপির দখলে! ফলত, পশ্চিমবঙ্গের গণতান্ত্রিক ভবিষ্যৎ যে প্রবল হুমকির মুখে, সে নিয়ে বিশেষ সন্দেহ থাকার কথা না।
তবুও, আতঙ্কে দিশাহারা হবার কারণ ঘটেনি, এবং স্বাভাবিক যুক্তিবিচার ও শুভবুদ্ধিতে আস্থা হারানোরও কোনও কারণ ঘটেনি। আশা করা যেতেই পারে, ক্ষমতাসীন সরকার সুশাসনে মন দিলে সরকার-বিরোধী নেতিবাচক ভোটটা হয়ত বিদ্বেষ-আশ্রয়ী রাজনীতির কবল থেকে বেরিয়ে আসবে, হয়ত বা উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোর ক্ষোভ মেটানোর সুবন্দোবস্ত হলে সেখানে বিজেপির জয়-জয়কারের বেলুন ফেঁসে যাবে। সে সাধ ও সাধ্য সরকারের আছে কিনা, তা অবশ্য সরকারি কর্তাব্যক্তিরাই ভাল বলতে পারবেন।
আরও আশা করা যেতে পারে, এ দেশে মৌলবাদী রাজনীতির বাকরোধকারী অগ্রগমনের এই পর্বটি হয়ত বা তার সেরা সময়টা পেরিয়ে এসেছে, হয়ত বা এবারে আস্তে আস্তে ভারতীয় সমাজ ও রাষ্ট্রদেহের আভ্যন্তরীণ ভারসাম্য-ব্যবস্থাগুলোর সঙ্গে তার সংঘর্ষ ক্রমেই প্রকট হয়ে উঠতে থাকবে। তাদের অধিকৃত রাজ্যগুলোতে মানুষের প্রতিষ্ঠানবিরোধী ক্ষোভ বেড়ে উঠবে, স্থানীয় দলগুলোর সঙ্গে তাদের জটিল ও অস্থিতিশীল বোঝাপড়াগুলো ভেঙে পড়তে থাকবে, প্রভাবশালী বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক লবির সঙ্গে বাধবে সংঘাত, এবং সেনা-আমলাতন্ত্র-বিচারব্যবস্থার সঙ্গে তাদের সুসম্পর্কও আর তত মসৃণ থাকবে না। ইতিমধ্যে, আন্তর্জাতিক চাপও হয়ত বাড়তে থাকবে। ফলত, পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে যেভাবে তারা সর্বশক্তি নিয়োগ করে রাজনৈতিক পরিসর দখল করার চেষ্টা করেছিল, সে প্রচেষ্টা দীর্ঘদিন বজায় রেখে চলাটা তাদের পক্ষে আর সম্ভব হয়ে উঠবে না।
আর, সর্বশেষ আশা, দেশের সমস্ত গণতন্ত্রপ্রিয় যুক্তিশীল কর্তৃত্ববাদ-বিরোধী নাগরিক তাঁদের বিচিত্র মত-পথ-বিশ্বাসের বেড়া ভেঙে দেশের সংকট মোচনে ক্রমশ একজোট হবেন, আটকে দেবেন দেশের সমস্ত রাষ্ট্রীয়-সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিসর অযুক্তি অন্ধত্ব আর বিদ্বেষের হাতে বেদখল হয়ে যাওয়ার এই প্রক্রিয়া, গণতন্ত্রের এই ভয়ঙ্কর বহ্ন্যুৎসব।
তবে, সে সবের জন্য, নিজে নিজে যুক্তি দিয়ে ভাবা, নিজে নিজে তথ্য যাচাই করে নেওয়া, এবং আবেগাশ্রয়ী মিথ্যে প্রচারের অংশ হতে অস্বীকার করাটা খুব জরুরি।
হ্যাঁ, এমন কি সে প্রচার মৌলবাদ বিরোধিতার নাম করে হলেও!
পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কিত নীতিঃ এই লেখাটি ছাপা, ডিজিটাল, দৃশ্য, শ্রাব্য, বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিলিপিকরণ বা অন্যত্র প্রকাশের জন্য গুরুচণ্ডা৯র অনুমতি বাধ্যতামূলক। লেখক চাইলে অন্যত্র প্রকাশ করতে পারেন, সেক্ষেত্রে গুরুচণ্ডা৯র উল্লেখ প্রত্যাশিত। - আরও পড়ুনপ্রসঙ্গ কোভিড ও ভ্যাকসিন : মাননীয় ষড়যন্ত্র-তাত্ত্বিক, আপনাকে বলছি স্যার - Debasis Bhattacharyaআরও পড়ুনইউরোপের বিজ্ঞান-প্রযুক্তি বিপ্লব কি ঔপনিবেশিক শোষণ ছাড়া কিছুতেই হতে পারত না? - Debasis Bhattacharyaআরও পড়ুনএক মুক্তিযোদ্ধার কাহিনী - দীপআরও পড়ুনইদবোশেখির লেখাপত্তর - গুরুচণ্ডা৯আরও পড়ুনবৈঠকি আড্ডায় ১৩ - হীরেন সিংহরায়আরও পড়ুনবৈঠকি আড্ডায় ১২ - হীরেন সিংহরায়আরও পড়ুনবৈঠকি আড্ডায় ১১ - হীরেন সিংহরায়
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
- পাতা : ১২
 ঐ | 2409:4060:218b:b00b::1dee:c0ac | ১২ মে ২০২১ ০০:৩২105876
ঐ | 2409:4060:218b:b00b::1dee:c0ac | ১২ মে ২০২১ ০০:৩২105876এই ভোটের ফল বেরোবার পর একইভাবে শ্রী দিলীপ ঘোষ, ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের হিসেবটি বিস্মৃত হয়েছেন। সেটা প্রবেশ করালে চিত্রগুলি ফেটে পড়বে।
 হেঁহেঁ | 65.175.106.2 | ১২ মে ২০২১ ০০:৩৫105877
হেঁহেঁ | 65.175.106.2 | ১২ মে ২০২১ ০০:৩৫105877কি বলি বলুন, এলেবেলেবাবুর মত কয়েকজন বিজ্ঞ পন্ডিত এসব গুজব ছড়ান হেঁহেঁ। তা ওনার রামনাম গাওয়া টিয়াপাখি ভোটের পর ফুড়ুৎ হয়ে গেল। তাপ্পর উনি নিজেই রাম থেকে বাম হয়ে গেলেন হেঁহেঁ।
 পর-শ্যু-রাম | 45.248.56.223 | ১২ মে ২০২১ ০১:২৫105878
পর-শ্যু-রাম | 45.248.56.223 | ১২ মে ২০২১ ০১:২৫105878সলিড যুক্তি। জমাটি বিশ্লেষণ। এখন কে কার চেয়ে ক-ছটাক বেশি বাম, তার কম্পিটিশনটা থামলে বাঁচি!
 দীপক মুক্তমনা | 2409:4060:2e09:d5b:89ae:fd7a:7abd:ec0d | ১২ মে ২০২১ ০৮:১১105880
দীপক মুক্তমনা | 2409:4060:2e09:d5b:89ae:fd7a:7abd:ec0d | ১২ মে ২০২১ ০৮:১১105880মাত্রাতিরিক্ত হ্যাজানো, বামেদের দোষ না খুঁজে অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপানোর পুরনো অভ্যেস।।
তোমার থেকে এরকম লেখা আশা করি নি।
 দীপক মুক্তমনা | 2409:4060:2e09:d5b:89ae:fd7a:7abd:ec0d | ১২ মে ২০২১ ০৮:১১105881
দীপক মুক্তমনা | 2409:4060:2e09:d5b:89ae:fd7a:7abd:ec0d | ১২ মে ২০২১ ০৮:১১105881মাত্রাতিরিক্ত হ্যাজানো, বামেদের দোষ না খুঁজে অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপানোর পুরনো অভ্যেস।।
তোমার থেকে এরকম লেখা আশা করি নি।
 তন্ময় দাশগুপ্ত | 223.223.139.183 | ১২ মে ২০২১ ০৮:৫৮105882
তন্ময় দাশগুপ্ত | 223.223.139.183 | ১২ মে ২০২১ ০৮:৫৮105882তথ্যবহুল লেখা। শানিত যুক্তি। তবু কিছু কথা যুক্ত করার ইচ্ছে রইল। তার আগে আমাকেও একটু তথ্য ঘেঁটে দেখতে হবে।
 দেবাশিস্ ভট্টাচার্য | 2401:4900:104d:b0b7:608f:9743:5fd:bd10 | ১২ মে ২০২১ ১১:৫৫105886
দেবাশিস্ ভট্টাচার্য | 2401:4900:104d:b0b7:608f:9743:5fd:bd10 | ১২ মে ২০২১ ১১:৫৫105886ভেবেছিলুম, সিপিএম লুকিয়ে তৃণমূলে ভোট দিচ্ছে এই তথ্য বার করলে তৃণমূল পুষ্পবৃষ্টি করবে। কিন্তু, অভাগা যেদিকে চায়, সাগর শুকায়ে যায়! ইদিকে, সিপিএম-এর নোকেরা নুকিয়ে তিনুকে ভোট দিচ্ছেন এটা সিপিএম-এর কাচেও ভারি ইয়ে ক্যাইস, তাঁরাও মোন খুলে আনন্দো কোত্তে পাচ্চেন্নাকো। ভারি সমোস্সা চাদ্দিকে, জানেন্তো!
 কাজরী রায়চৌধুরী | 45.112.69.215 | ১২ মে ২০২১ ১২:৪৪105887
কাজরী রায়চৌধুরী | 45.112.69.215 | ১২ মে ২০২১ ১২:৪৪105887খুবই যুক্তিনিষ্ঠ লেখা। শেষের বাক্যটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। নিজে নিজের ভিতরের যুক্তিকে শানিয়ে তোলা এবং আবেগাশ্রয়ী মিথ্যেকে বুঝতে পারা এবং প্রশ্রয় না দেওয়া এখন আমাদের প্রধান কর্তব্য।
 Pinaki | 136.228.209.46 | ১২ মে ২০২১ ১৭:৪৮105893
Pinaki | 136.228.209.46 | ১২ মে ২০২১ ১৭:৪৮105893হিসেবটা আসন ধরে ধরে করলে অনেক ক্ষেত্রেই এই লেখার প্রতিপাদ্য চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে। দেখি সেরকম কিছু আসনের ছবি পরে দেওয়ার চেষ্টা করব। তবে সেগুলো ২০১৬ র সাথে ২০১৯ এর রেজাল্ট তুলনা করে। ২০২১ এ অনেক হিসেব উল্টেছে।
 দেবাশিস্ ভট্টাচার্য | 103.217.235.226 | ১২ মে ২০২১ ২১:৪৫105902
দেবাশিস্ ভট্টাচার্য | 103.217.235.226 | ১২ মে ২০২১ ২১:৪৫105902২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে পৃথিবী উল্টে গেলেও তাতে ২০১৬ আর ২০২১ বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলের অর্থ বিন্দুমাত্র বদলাবে না --- আমার এমনটাই ধারণা। তবু, নতুন তথ্যযুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করতে চাইলে করুন না প্লিজ। সেটা সব সময়েই কাম্য।
-
sagnik ray choudhury | ১৩ মে ২০২১ ০৫:৩২105907
- তৃণমূল থেকে গেছে আটচল্লিশটি আসন (প্রায় বাষট্টি শতাংশ) এবং কংগ্রেস থেকে পনেরোটি (প্রায় কুড়ি শতাংশ), সেখানে সিপিএম থেকে গেছে মাত্র ছয়টি (প্রায় আট শতাংশ) এবং বাকি বামদলগুলোকে ধরলে সব মিলিয়ে প্রায় বারো শতাংশ। অর্থাৎ, এর মধ্যে প্রায় বিরাশি শতাংশ অবদানই যে অ-বাম দলের, সে নিয়ে বোধহয় আর কোনও কথাই হওয়া উচিত নয়।
এ কিরকম হিসেব? ২০১৬ তে লেফট ফ্রন্টের টোটাল সিট ছিল ২৬টা, তার মধ্যে মুভ করেছে ৯ টা। তৃণমূলের ছিল ২১১টা, তার মধ্যে মুভ করেছে ৪৮টা। ৩৪% বনাম ২২% । যে দল ২৬ টা সিট পায়, তার পক্ষে খুব কষ্ট করে হলেও ২৬/৭৭ অর্থাৎ ৩৩% এর বেশী অবদান রাখা সম্ভব নয় ভোট মুভমেন্ট এ। এনারা সংখ্যাগুরু অর্থাৎ ৫০% অবদান রাখবেন কি করে?
 দেবাশিস্ ভট্টাচার্য | 2401:4900:1043:cb3:4cef:3a55:bbe7:f1f2 | ১৩ মে ২০২১ ০৮:৫৬105910
দেবাশিস্ ভট্টাচার্য | 2401:4900:1043:cb3:4cef:3a55:bbe7:f1f2 | ১৩ মে ২০২১ ০৮:৫৬105910প্রশ্নটা বুঝিনি। ২৬-টা আসন বামফ্রন্টের নয়, সিপিএম-এর একারই। তা থেকে বিজেপিতে চলে যাওয়া আসন ৯-টা নয়, ৬-টাই। লেখাটা ভাল করে পড়ুন। পুরো ২৬-টি আসনই বিজেপিতে চলে গেলে কী হতে পারত বা পারত না সে প্রশ্ন খুব প্রাসঙ্গিক বলে মনে হল না।
 র২হ | 49.37.3.248 | ১৩ মে ২০২১ ১০:৫০105913
র২হ | 49.37.3.248 | ১৩ মে ২০২১ ১০:৫০105913নো ভোট টু বিজেপি স্লোগানের বিরোধিতাকে বিজেপি সমর্থন বলেই মনে করি।
স্লোগান, পরিসংখ্যান সবই ইন্টারপ্রিটেশন নির্ভর।
 দেবাশিস্ ভট্টাচার্য | 2401:4900:3140:d2df:41d3:70:1d96:8cf | ১৩ মে ২০২১ ১২:০৫105915
দেবাশিস্ ভট্টাচার্য | 2401:4900:3140:d2df:41d3:70:1d96:8cf | ১৩ মে ২০২১ ১২:০৫105915তথ্য থেকে কীভাবে সত্যে পৌঁছতে হয় সেটা না শিখতে পারলে আমরা কোনও দিনই মৌলবাদী রাজনীতির সত্যিকারের বিরোধিতা করবার যোগ্য হয়ে উঠতে পারব না, শুধু 'আমি ওর পক্ষে আর তোর বিপক্ষে' বলে চেঁচিয়ে ক্ষুদ্র অর্থহীন হাস্যকর কলহে মাততে পারব।
 র২হ | 49.37.3.248 | ১৩ মে ২০২১ ১২:১৪105916
র২হ | 49.37.3.248 | ১৩ মে ২০২১ ১২:১৪105916তাহলে তে পৌঁছনোর পথ নিয়ে ঐকমত্য হতে হবে। জনমানস নিয়ে কি আর বাইনারি হয়, ইন্টারপ্রিটেশন, পারসেপশন সবই দেখতে হবে। সত্য কার কাছে কী, আর্বান আপওয়ার্ড মোবাইল অ্যাসপিরেন্ট, সম্পন্ন চাষী, চা বাগানে শ্রমিক - সবার সত্যও মিলতে হবে।
পরিসংখ্যান আর এমপ্যাথির মধ্যে দূরত্ব না থেকে যায়।
 দেবাশিস্ ভট্টাচার্য | 2401:4900:3140:d2df:41d3:70:1d96:8cf | ১৩ মে ২০২১ ১২:৩০105917
দেবাশিস্ ভট্টাচার্য | 2401:4900:3140:d2df:41d3:70:1d96:8cf | ১৩ মে ২০২১ ১২:৩০105917বুঝলাম, কিন্তু পরিসংখ্যান তো আর এমপ্যাথি দিয়ে তৈরি হতে পারবে না, কাজেই এমপ্যথিকেই পরিসংখ্যানের কাছে পৌঁছবার মত প্রশিক্ষিত হয়ে উঠতে হবে।
 ভোটবদল | 2405:8100:8000:5ca1::c1:f8e7 | ১৩ মে ২০২১ ১২:৩১105918
ভোটবদল | 2405:8100:8000:5ca1::c1:f8e7 | ১৩ মে ২০২১ ১২:৩১105918পশ্চিমবঙ্গে বামেদের ভোট - কিছু গেছে বিজেপিতে, কিছু গেছে তৃণমূলে। আর কতদুরেই বা যাবে, কার কাছেই বা যাবে!
-
sagnik ray choudhury | ১৩ মে ২০২১ ১২:৪৯105919
- অর্থাৎ, এর মধ্যে প্রায় বিরাশি শতাংশ অবদানই যে অ-বাম দলের, সে নিয়ে বোধহয় আর কোনও কথাই হওয়া উচিত নয়।
বক্তব্য হচ্ছে বাম দল কোনো ভাবেই ৩৪% এর বেশী অবদান রাখতে পারতো না, ৫০%, অর্থাৎ মেজরিটি অবদান তো অনেক দূর। মুশকিল হচ্ছে আপনি ২০১৬ এ প্রাপ্ত টোটাল সিটের বেসিসে ভোট ট্রান্সফারের কন্ট্রিবিউশন দেখছেন (অবাম ৮২%, বাম ১২%), শতাংশের হিসেবে নয়, যেটা দেখা উচিত। শতাংশের হিসেবে দেখলে তৃণমূলের বিজেপি তে সিট ট্রান্সফার সিপিএম এর থেকে কম। এই সমস্যাটা কি ক্লিয়ার? এর সঙ্গে পুরো লেখা পড়ার কোন সম্পর্ক নেই।
 sm | 2402:3a80:aaa:679b:0:5a:96b1:7c01 | ১৩ মে ২০২১ ১২:৫১105920
sm | 2402:3a80:aaa:679b:0:5a:96b1:7c01 | ১৩ মে ২০২১ ১২:৫১105920বামেরা লোকসভা আর বিধান সভায় শূন্য আসন পেয়েছে।এখন বামেদের ভোট রামের ঝুলি তে গেলো কি তিনো দের কাছে গেলো; এটা এখন বিরাট কিছু ইস্যু নয়। বরঞ্চ বামেদের ফান্ডিং নিয়ে আলোচনা চলতে পারে।
 দেবাশিস্ ভট্টাচার্য | 2401:4900:3140:d2df:41d3:70:1d96:8cf | ১৩ মে ২০২১ ১২:৫১105921
দেবাশিস্ ভট্টাচার্য | 2401:4900:3140:d2df:41d3:70:1d96:8cf | ১৩ মে ২০২১ ১২:৫১105921হাঃ হাঃ হাঃ - জব্বর বলেছেন কিন্তু !
-
রৌহিন | ১৩ মে ২০২১ ১২:৫২105922
এসবের চেয়ে অনেক সহজ তো বিশ্বাস করে নেওয়া যে "বাম ভোট রামে গেছে" - তাতে মানও বাঁচে, সময়ও। মানুষকে ভাল থাকতে দেবেন না?
 দে-ভ | 2401:4900:3140:d2df:41d3:70:1d96:8cf | ১৩ মে ২০২১ ১২:৫৩105923
দে-ভ | 2401:4900:3140:d2df:41d3:70:1d96:8cf | ১৩ মে ২০২১ ১২:৫৩105923ভোটবদল, আপনাকে বললাম
 দে-ভ | 2401:4900:3140:d2df:41d3:70:1d96:8cf | ১৩ মে ২০২১ ১২:৫৫105924
দে-ভ | 2401:4900:3140:d2df:41d3:70:1d96:8cf | ১৩ মে ২০২১ ১২:৫৫105924রৌহিন, আপনাকেও
 অর্জুন সেনগুপ্ত | 45.250.247.112 | ১৩ মে ২০২১ ১৩:৫৭105926
অর্জুন সেনগুপ্ত | 45.250.247.112 | ১৩ মে ২০২১ ১৩:৫৭105926সুহৃদ, ভাতৃপ্রতিম দেবাশীষের 'বাম--ভোট রাম হয়ে যাওয়ার গুজব' -- একটি পোস্ট ট্রুথ প্রোপাগাণ্ডা, একটি উৎসাহব্যঞ্জক আলোচনা, কৌতুহল উদ্দীপকও বটে। তবে সংখ্যার সিঁড়ি বেয়ে সিদ্ধান্ত উপনীত হতে আমার স্বস্তি হয়না। সংখ্যা খুব শয়তান, কখন যে কাকে কাত করে দেয় কেউই জানেনা। আমি কিন্তু দেবাশীষকে Statistical fool বলছিনা মোটেও। সে সেসব খুব জানে। তাইতো তার কথনে এত কিন্তু আছে। আসলে সংখ্যার উপর বাজি রাখা এক বৈজ্ঞানিক বিড়ম্বনা আর দেবাশীষ যে বৈজ্ঞানিক তা নিয়ে কোনো বিতর্ক হবেনা। যাক ওকে একটু বকে নিজের বকবকানি শুরু করি।
শুরুতে একটি ঘোষণা ও একটি প্রশ্ন --- ভোট কারো বাবার নয়, প্রশ্ন হলো -- বাম কয় কারে?
উত্তর হলো, প্রতিষ্ঠানকে যে প্রশ্ন করে ও যথাযথ উত্তর না পেলে যে ব্যক্তি বা সমষ্টি তার বিরোধিতা করে তাকেই বলে বাম। এই সংজ্ঞাই মোটামুটি স্বীকৃত।
চৌত্রিশ বছর ধরে আমরা দেবাশীষ বর্ণিত বামেদের দেখেছি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি রূপে। ভুলে গেছি মরিচঝাঁপি, বাইলাডিলা, বরানগর, এসপ্লানেড ইস্ট, সিঙুর, নন্দীগ্রাম, নেতাই, ধানতলা, বানতলা? বাম!! সে আমলে বন্ধ হয়েছে কয়েক'শ কারখানা। কোনো প্রতিবাদ হয়নি। বরংচ বাম পুলিশ প্রতিবাদীদের পিটিয়ে পোস্তা বানিয়েছে। মানে যারা মৃদু প্রতিবাদ করেছে। জলের দরে পাওয়া জমি শিল্পপতিরা ফ্ল্যাট বানিয়ে কোটি কোটি কামিয়েছে। শ্রমিকরা পি এফ, গ্রাচুয়িটি ইত্যাদি না পেয়ে চোখের জল ফেলেছে। জলাঞ্জলি গিয়েছে তাদের পরিবার। এনিয়ে আমার সংগে কেউ দন্ত বকশিত করতে আসবেননা। বত্রিশ বছর ডিঃ অব ফ্যাকটরিজে চাকরি করেছি। বাম!! সর্বশেষ কংগ্রেসের সাথে connivance, মুসলিম মৌলবাদীদের সাথে মাখামাখি এদের বাম নাম সত্য হায় করে দিয়েছে মানে বামত্ব বেমালুম মুছে দিয়েছে।
অবশ্য আমরা যারা ক্ষমতার এঁড়ে বাছুর নই, আজীবন এড়িয়ে গেছি তাকে সেরকম বামেদের একটা bias আছে। আমদের যখন ষোলো সতেরো, অর্থাৎ যে বয়সে মানুষ সবচে প্রতিষ্ঠান বিরোধী হয় তখন পশ্চিম বঙ্গে প্রতিষ্ঠানের পাণ্ডা হলো সিপিএম। তাদের মৌরসীপাট্টা, মুরুব্বিয়ানা, গুণ্ডাগর্দি, হার্মাদি আচরণ আমাদের মতো বামেরা তাদের আজীবন নির্বাসন দিয়েছে। এমনকি ঐ দলের ক্যাডার যারা ক্ষমতার ক্ষীরের ভাগ পায়নি তারাও ক্ষেপে ছিলেন বিলক্ষণ। ঝোপ বুঝে মেরেছে কোপ। বলুন তো সিপিএম এন্ড কোং--এর ক্রিয়াকলাপ দেখে যারা বহুদিন তাদের ভোট দিয়েছে তারা কি বাম ভোটার? ষাট সত্তরের আন্দোলনের ঘি শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে? ঠকঠকালে পাবি কী? পশ্চিম বঙ্গে বামই বিদায় নিয়েছে বহুদিন, তো বাম ভোটারদের পরিযায়ী পাখা মেলা নিয়ে সংখ্যা তত্ত্বের পটপটানি।
বলবেনতো ভূমি সংস্কার ইত্যাদি ; সংস্কারী যদি বাম হয় তবে এক পিসও ডান নেই ভাই। যে সাথী, শ্রী--র সিরিয়াল নামিয়েছে দুমদাম তাতে মমতা তো মহাবাম। সে অর্থে বিহারের নীতিশের থেকেও 'বামেরা' কত বাম তা মাপতে হয় নিক্তিতে।
পশ্চিম বঙ্গে বহুদিনই সব ডান ভোট। বিভেদটা শুধু দলে। ঐ ইস্ট -- মোহন মার্কা আরকি! ভোট কাকে দি-- দাদু খায়, নাতি খায়..........
এরাজ্যে বাম ও বাম ভোটার বিলুপ্ত হয়েছে বহুদিন। দেবাশীষের তুলনা ২০১৬ ও ২১--এর মধ্যে। কিন্তু মাঝে একটা ২০১৯ আছে। সেখানেই বাম নামধারীদের ভোট জোট বেঁধে পড়েছে বিজেপিতে। বলছি নব্বইয়ের দশক থেকেই সিপিএমের ভোট সরতে শুরু করেছে। আজ তার গতিবিধির স্বরূপ সংখ্যায় সামলানোর চেষ্টা বৃথা।
দেবাশীষের দোষ নেই। বাম নামক একটি কল্পিত প্যারাডাইম নিয়ে পণ্ডশ্রম করেছে। বাম ভোটের গঙ্গাপ্রাপ্তি হয়েছে বহুদিন। আর ভোট কারো বাবার নয়।
২০২১--এ শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ শিয়রে শমন অনুভব করে 'নো ভোট টু বিজেপি' করেছে। বাকিরা কী করেছে বলা মুশকিল। তবে যে যেখানেই যাক বাম দিক থেকে কোথাও যায়নি।
আজ সিপিএমের ভোট কোথায় গেল তা ভগাই জানে!!!
 দেবাশিস্ ভট্টাচার্য | 103.217.235.152 | ১৩ মে ২০২১ ১৪:০১105927
দেবাশিস্ ভট্টাচার্য | 103.217.235.152 | ১৩ মে ২০২১ ১৪:০১105927- এই সমস্যাটা একদমই ক্লিয়ার না, এবং এর সঙ্গে পুরো লেখাটা পড়ার সম্পর্ক বড্ড বেশি মজবুত। প্রথমত, সিপিএম-এর ছাব্বিশটার মধ্যে মাত্র ছটা গেছে এটাই ঘটনা, পুরোটা গেলে কী হতে পারত সেটা অবান্তর, এবং কী হতে পারত না সেটা আরওই অবান্তর। আসনের সংখ্যার পরমমান এবং শতাংশ --- লেখা থেকে কোনওটাই বাদ পড়েনি, নিশ্চিন্ত থাকুন।
 দেবাশিস্ ভট্টাচার্য | 2401:4900:3148:5391:a729:a605:8b74:f0b5 | ১৩ মে ২০২১ ১৪:৫৪105929
দেবাশিস্ ভট্টাচার্য | 2401:4900:3148:5391:a729:a605:8b74:f0b5 | ১৩ মে ২০২১ ১৪:৫৪105929 অর্জুনদা, তোমার মতামত শ্রদ্ধা করি, এবং তোমার কর্মকাণ্ডকে আরওই শ্রদ্ধা করি। তুমি অতিশয় ব্যস্ত মানুষ, আমার লেখার মত তুচ্ছ বস্তু নিয়ে তোমাকে বিব্রত করতে রীতিমত অপরাধ বোধ হয়। কিন্তু, মন্তব্য করার সময় পেয়েছ বলেই সাহস করে জিজ্ঞেস করি, লেখাটি কি আদৌ পড়ে উঠতে পেরেছ?
-
sagnik ray choudhury | ১৩ মে ২০২১ ১৫:০১105930
লেখাটার মূল প্রশ্ন হচ্ছে যে ৩২% ভোট তৃণমূল ও বিজেপি বিরোধীরা ক্ষয় করেছে (২০১৬ র ভোটের রেস্পেক্টে), সেটা কোথায় গেছে। সেটার জন্যে একটা হাইপোথিসিস হচ্ছে যে এট লিস্ট ১৬% তৃণমূলে গেছে। সেই হাইপোথিসিস প্রুভ করার উপায় হচ্ছে যে ২০১৬ সালের থেকে বামেদের ৬৭% সিট, এবং কংগ্রেসের সেরকমই কিছু একটা হবে, হিসেবে করিনি, তৃণমূলে গেছে।
প্রথম কথা হচ্ছে যে এই ভাবে গড় সিটের বেসিসে শতাংশের হিসেব করা মুশকিল, সেটা সকলেই জানেন। এই জন্যেই পিনাকী উপরে সিট ধরে ধরে ভোট শতাংশ দেখার কথা বলেছিলেন।
কিন্তু আমি সেই জায়গাটায় যাচ্ছিইনা। আপনি এই স্টেটমেন্ট টা দিয়েছেন: “ অর্থাৎ, এর মধ্যে প্রায় বিরাশি শতাংশ অবদানই যে অ-বাম দলের, সে নিয়ে বোধহয় আর কোনও কথাই হওয়া উচিত নয়।” এটা প্রথমে পড়ে মনে হবে সিট চেঞ্জে, (শতাংশ নয়, সিট চেঞ্জে) অবাম দল গুলির “অবদান" বেশী। এর মধ্যে একটা ফ্যালাসি আছে। অবদান কে যদি আপনি টোটাল সিটের মুভমেন্ট হিসেবে দেখেন, তাহলে অবশ্যই অ-বাম দল গুলির অবদান বেশী। কিন্তু ব্যাপারটা তো এরকম নয়, সিপিএম এর সিট ছিল ২৬ টা, এই নিয়ে ৭৪টা সিটে কি “অবদান” রাখা যেত? খুব বেশী হলে ৩৪% . যদি একজ্যাক্টলি সেটাই হতো, অর্থাৎ সিপিএম এর ২৬টা সিটই বিজেপিতে মুভ করতো, তাহলেও অ-বাম দলের “অবদান" হতো ৬৬%, যা সিগ্নিফিক্যান্টলি বেশী। সেই পরিস্থিতিতেও কি আপনি একই কথা বলতেন? “অবদান” তো সম্পদের শতাংশের হিসেবে গণনা হওয়া উচিত। সেটা যদি করেন, তাহলে দেখুন সিপিএম থেকে সিট মুভ করেছে ৬/২৬, টিএমসি থেকে ৪৮/২১১, দুটোই রাফলি ২৩% . এই হিসেবটা আপনি পরে দেখিয়েছেন, কিন্ত সেটা আপনার ওই স্টেটমেন্টটাকে কন্ট্রাডিক্ট করছে। সুতরাং ওই স্টেটমেন্টটা নিয়েই আপত্তি আছে আমার।
বেসিক দুটো প্রশ্ন: ১. তৃণমূলের ২০১৬ র ভোটব্যাংক অক্ষত আছে কিনা? ২. বাম ভোটাররা টিএমসিকে ভোট দিয়েছেন কিনা? ইন্টুইটিভলি প্রথমটার উত্তর না, দ্বিতীয়টার উত্তর হ্যাঁ। কিন্তু গড় সিটের হিসেব থেকে সেটা প্রমাণ করা শক্ত। যাকগে এই আলোচনায় আর শক্তিক্ষয় করবো না।
 অর্জুন সেনগুপ্ত | 223.191.33.186 | ১৩ মে ২০২১ ১৭:৪৪105934
অর্জুন সেনগুপ্ত | 223.191.33.186 | ১৩ মে ২০২১ ১৭:৪৪105934দেবাশীষ লেখাটা আমি তিনবার পড়েছি। তোমার প্রতিপাদ্য বিষয় বাম ভোট অধিকাংশ বিজেপি নয়, তৃণমূলে পরিবর্তিত হয়েছে। তুমি ২০১৬ ও ২০২১ --এর মধ্যে তুলনা করেছ। আমি বোধহয় আমার বক্তব্য স্পষ্ট করে বোঝাতে পারিনি। বাম ভোট বিজেপি বা তৃণমূলে যাওয়ার মধ্যে শুধু সংখ্যার অদলবদল নয়, মতাদর্শের পরিবর্তনও বোঝায়। সেই পরিবর্তন শুধু সংখ্যাতত্ত্বের নিরিখে ব্যক্ত হয়না। তার আরও গভীর তাৎপর্য থাকে যা আবার সংখ্যাকে প্রভাবিত করে। আমি বলতে চেয়েছি তোমার আলোচনার ভিত্তিটিই সঠিক নয়। বাম ভোট ডানে যায়নি। ডান ভোটই ডানে গেছে কারণ আশীর দশক থেকেই বাম আর বিন্দুমাত্র বাম নেই এ দেশে। সাংখ্যিক গণনের ক্ষেত্রেও এতে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়।
আমি এখানে শুধু শব্দের জাগলারি করতে যাইনি। আসলে' বাম' থেকে ভোটসিফ্ট শুরু হয়েছে ২০০৬ পরবর্তী পর্যায়ে বা তার একটি জোরদার প্রবণতা শুরু হয়েছে। তারই একটি অন্তিম রূপ দেখা যাচ্ছে ২০২১-এ। আমি বলতে চেয়েছি শেষ পাঁচ বছরের পরিসংখ্যান দিয়ে প্রকৃত চিত্র ধরা যাবেনা। ২০১৬-তে যে তৃণমূলী ভোট তার মধ্যেও প্রচুর তথাকথিত বাম ভোট ঢুকে আছে। আসলে অন্তত ভারতবর্ষে কোনো দলের ভোটব্যাঙ্ক বলে কিছু হয়না। বাম ভোট ও তৃণমূলী ভোটের কোনো মেরুকরণ হয়না। তাই পাঁচ বছর ভিত্তিক হিসাব প্রকৃত চিত্রের পরিচায়ক নয়।
 দেবাশিস্ ভট্টাচার্য | 103.217.235.178 | ১৩ মে ২০২১ ২০:১৩105937
দেবাশিস্ ভট্টাচার্য | 103.217.235.178 | ১৩ মে ২০২১ ২০:১৩105937sagnik,
আমি আর আপনি এতক্ষণ যা কথাবার্তা বললাম, তা থেকে মনোযোগী পাঠক সম্ভবত যা বোঝার বুঝে ফেলতে পারবেন। কাজেই, আর আলোচনায় শক্তিক্ষয় করবেন না বলে যে সিদ্ধান্তটা নিয়েছেন, সেটা আমার মতে সঠিক --- আমিও একই সিদ্ধান্ত নিলাম।
 দেবাশিস্ ভট্টাচার্য | 103.217.235.178 | ১৩ মে ২০২১ ২০:২২105938
দেবাশিস্ ভট্টাচার্য | 103.217.235.178 | ১৩ মে ২০২১ ২০:২২105938অর্জুনদা,
তুমি শব্দের জাগলারি করছ এমন অভিযোগ মোটেই করিনি। আর, আমার লেখাটা পড়েছ কিনা এ প্রশ্নও মোটেই তোমার পড়াকে কটাক্ষ করার জন্য নয়, অপরাধ নিও না। আসলে, এ ব্যাপারে তোমার অবস্থান আমি জানি, এবং সেটা এখানে যেভাবে প্রকাশ পেয়েছে, তুমি আমার তথ্য-যুক্তি খুঁটিয়ে অনুধাবন না করলেও তা ওভাবেই প্রকাশ পেতে পারত --- এই জন্যে প্রশ্নটা করেছিলাম। যাই হোক, আমার যা বলার তা পরে বলছি, সবিস্তারে।
- পাতা : ১২
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
-
গুরুচণ্ডা৯-র গ্রাহক হোন
কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে গুরুচণ্ডা৯-র গ্রাহক হোন। গুরুচণ্ডা৯তে প্রকাশিত লেখাগুলি পেতে চাইলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যুক্ত হোন, অথবা, আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলটির গ্রাহক হোন।
- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই
- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... )
(লিখছেন... অরিন)
(লিখছেন... kk, রমিত চট্টোপাধ্যায়, বিপ্লব রহমান)
(লিখছেন... Aranya )
(লিখছেন... )
- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন
(লিখছেন... সৃষ্টিছাড়া, সমরেশ মুখার্জী)
(লিখছেন... haridas, Prabhas Sen, Ranjan Roy)
(লিখছেন... সমরেশ মুখার্জী, Kishore Ghosal, সমরেশ মুখার্জী)
(লিখছেন... Muhammad Sadequzzaman Sharif, Muhammad Sadequzzaman Sharif, দীপ)
(লিখছেন... dc, পলিটিশিয়ান, dc)
- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... )
(লিখছেন... )
(লিখছেন... jsl)
(লিখছেন... অরিন, &/, অরিন)
(লিখছেন... lcm, পাঠক, সুকি)
- কি, কেন, ইত্যাদি
- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...
- আমাদের কথা
- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...
- বুলবুলভাজা
- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...
- হরিদাস পালেরা
- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...
- টইপত্তর
- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...
- ভাটিয়া৯
- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...
- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।