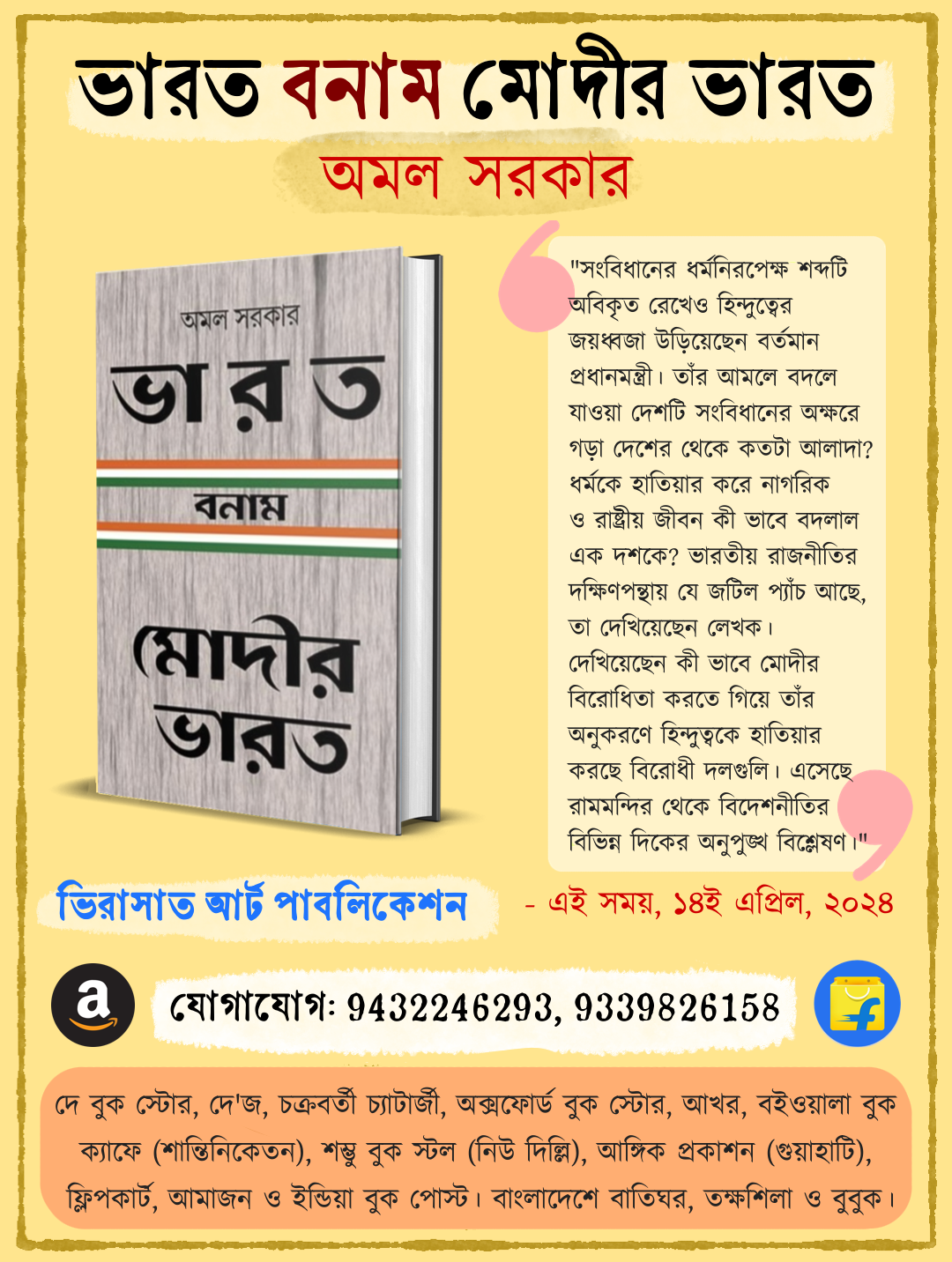- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
 মলয় রায়চৌধুরী | 27.58.255.50 | ১০ আগস্ট ২০২১ ১৯:১৭734845
মলয় রায়চৌধুরী | 27.58.255.50 | ১০ আগস্ট ২০২১ ১৯:১৭734845জাঁ জেনে সম্পর্কে জাঁ পল সার্ত্রে : মলয় রায়চৌধুরী
ফেলিক্স গুত্তারি তাঁর ‘জেনে রিগেইনড’ বইতে সার্ত্রের ‘সেইন্ট জেনে: অ্যাক্টর অ্যাণ্ড মার্টিয়ার’ ( ১৯৬৩ ), ৬৫০ পৃষ্ঠার বইটাকে বলেছেন ‘সার্ত্রের তৈরি জেনের বিরাট ও অতীব ব্যয়বহুল সমাধিস্তম্ভ’ । টাইম ম্যাগাজিন অবশ্য বলেছিল ‘এ পর্যন্ত লেখা বিস্ময়কর সমালোচনামূলক গবেষণার অন্যতম।’ বইটা সম্পর্কে জেনে বলেছেন যে তিনি সন্ত নন, অভিনেতা নন, শহিদও নন ; তিনি একজন শ্রমজীবি লেখক । সার্ত্রে বলেছেন, ‘জেনে হলেন ঈশ্বর’। লুই ফার্দিনাঁ সেলিন বলেছেন, ‘ফরাসি দেশে কেবল দুজন লেখক আছেন, জেনে এবং আমি।’
জেনেকে নিয়ে এডমাণ্ড হোয়াইটও পরে ৮০০ পৃষ্ঠার একটি বই লিখেছেন। সার্ত্রে যেন এইরকম চরিত্র খুঁজছিলেন যার ওপরে নিজের দর্শন চাপিয়ে তিনি নিজেকেই ব্যাখ্যা করতে পারেন। তিনি জেনেকে অস্তিত্ববাদী দার্শনিকের মোড়কে পুরেও তাঁকে বের করে এনেছেন মিথ্যাবাদী, পায়ুবিক্রেতা ও ক্রেতা, নাট্যকার, অভিনেতা, চোর, সাহিত্যিক ইত্যাদি থেকে তাঁর ব্যক্তিগত অস্তিত্ববাদী নায়ককে । বইটা এতো দীর্ঘ যে মাঝে-মাঝে বিরক্তিকর লাগলেও, থেমে থেমে চিন্তার অবসর নিতে হয় ফরাসি ‘ভদ্র, সুনীতিসম্পন্ন, বিবেচক’ সমাজ থেকে বহুকাল অন্ধকারে ছাঁটাই করা জেনে নামের এই মানুষটার অন্তরজগতের সাংঘাতিক, ভয়ানক, আতঙ্কজনক প্রবণতার তলায় চাপা পড়া লোকটাকে জানবার জন্য । সার্ত্রের চোখে জেনে একজন মৌলিক অস্তিত্ববাদী নায়ক হিসাবে প্রতিভাত হন, তার কারণ জেনে শয়তানি বা পাপ বা ইভিল করার মাধ্যমেই আবিষ্কার করতে সফল হন যে প্রকৃতপক্ষে খ্রিস্টধর্মের শয়তানি ও পাপ এবং রাষ্ট্রের চোখে অপরাধ ও ইভিল কাকে বলে । সার্ত্রের মতে, জেনে জন্মেছিলেন একটি অর্থহীন, পরিপন্হী জগতে, যা ভয়, আত্মদোষ, কলুষ, কল্মষ ও ইভিলে ঠাশা এবং এই প্রতিষ্ঠান থেকে ছাড়া পেতে হলে এই কাজগুলোর ভেতরেই দোল খেয়ে তার বিরোধিতা করতে হবে ।
জাঁ জেনের জীবনের চরম বিকৃতিগুলোকে জেনের তৈরি করা কিংবদন্তি থেকে আলাদা করে আসল মানুষটাকে বের করে আনার জন্য এডমাণ্ড হোয়াইট জেনের বন্ধুবান্ধব, প্রেমিকের দল, প্রকাশক এবং পরিচিতজনদের থেকে প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন, এবং চিঠিপত্র, সাক্ষাৎকার, জার্নাল, পুলিশের নথিপত্র, মনোবিদদের প্রতিবেদন যাচাই করে ৮০০ পাতার বই লিখেচিলেন যা সার্ত্রের থেকে একেবারে ভিন্ন অথচ গোয়েন্দা বইয়ের মতন আকর্ষক । তিনি জেনের প্রাণচঞ্চল প্রেরণার পরস্পরবিরোধিতাকে জীবনের ঘটনা থেকেই বের করে আনতে চেয়েছেন : সত্যতা ও ভণ্ডামি, বিশ্বস্ততা ও ছিনালি, কতৃত্ব ও নতিস্বীকার, সন্মান ও বেইমানি।
ফরাসি ভাষায় সার্ত্রের ( ১৯৫২ ) বইটিতে ‘কমেদিয়েন’ শব্দটি ব্যবহৃত যা ইংরেজিতে করা হয়েছে ‘অ্যাক্টর’, মূলত ‘দি থিফস জার্নাল’-এর ওপর ভিত্তি করেই জেনেকে বিশ্লেষণ করেছেন সার্ত্রে । জেনের বইটি, সার্ত্রে বলেছেন, প্রমাণ করে যে, প্রতিভা মানুষের প্রকৃতিদত্ত গুণ নয়, তা একটা পথ যা একজন লোক মরিয়া অবস্হায় আবিষ্কার করে । সার্ত্রে তাঁর ‘দি ডেভিল অ্যাণ্ড দি গুড লর্ড ( ১৯৫১ ) নাটকে গেৎজ চরিত্রটি জেনের মানসিকতা ও নৈতিকতার বোধ থেকে আহরণ করে লিখেছিলেন । আলোচক ডেভিড হ্যালপেরিন সার্ত্রের বইটি সম্পর্কে বলেছেন যে এটি একটি একক প্রতিস্বের সূক্ষ্ম, অসাধারণ এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান আর সেই সঙ্গে সমকামীদের লৈঙ্গিক অবস্হানের সামাজিক-দার্শনিক বিশ্লেষণ ।
বইটা চারটে পর্বে বিভাজিত । প্রথম হলো ‘মেটামরফোসিস’ ; দ্বিতীয় ‘ফার্স্ট কনভারশান : ইভিল’ ; তৃতীয় ‘সেকেণ্ড মেটামরফোসিস : এসথেটে’ এবং চতুর্থ ‘থার্ড মেটামরফোসিস : দি রাইটার’। প্রথম পর্বে, অনাথ ও জারজ জেনের বিভিন্ন পালক পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কের জটিলতা ও সীমাবদ্ধ জীবনধারা চিত্রিত করা হয়েছে যার সঙ্গে জেনে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারছেন না । সামাজিক ও সরকারি সংস্হাগুলোর সঙ্গে জেনের পরিচয় হয় এবং সংস্হাগুলো বালকটিকে সামাজিক সরঞ্জামে পালটে ফ্যালে । ফরাসি সরকার তার তত্বাবধায়ক জানার পর বালকটি হয়ে ওঠে পালক পরিবারদের অবাধ্য এবং সংশোধনের অযোগ্য, যার দরুন সরকার তাকে ছাপ্পা দেয় ‘অভ্যাসগত অপরাধীর’ । জেনের কৈশোর ও তারুণ্যে প্রশাসন তাকে অবিরাম পিষে ফেলতে থাকে আর তরুণটি হয়ে ওঠে ভয়প্রদর্শনকারী । সে আর একা থাকে না, তার মেটামরফোসিস হয়, সমাজের নানা অপরাধী তার বন্ধু হয়ে ওঠে এবং বুঝতে পারে যে এই অপরাধীরা তাদের অপরাধের মাধ্যমে রাষ্ট্রযন্ত্রের কাছে আত্মসমর্পিত । জেনে অস্পষ্টভাবে বুঝতে পারেন যে আইনত, প্রশাসনিকস্তরে এবং রাষ্ট্রের রসায়ানাগারে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য তিনি নির্বাচিত প্রাণী। সার্ত্রে বলেছেন যে জেনের প্রথম চুরিগুলো জেনের অন্তরজীবনের আবহ গড়ে তুলেছিল এবং তা হলো আতঙ্কের আহ্লাদ ।
বইটির দ্বিতীয় পর্বে, সার্ত্রের দার্শনিকতার মাল হয়ে ওঠেন জেনে । সার্ত্রে ব্যাখ্যা করেন ইভিল বা শয়তানি বা পাপের দার্শনিক ও তাত্বিক জটিলতা । বইয়ের এই পর্বটা বেশ দীর্ঘ আর ক্লান্তিকর । জীবনী থেকে দর্শন টেনে আনেন সার্ত্রে, বিশ্লেষণ করেন নৈতিকতা, অপরাধ, যৌনকামনা এবং অন্ধকার জগতের নানা এলাকায় জেনের মতন মানুষদের একের পর এক অবিরাম দুর্ভাগ্য ও অশান্তি । জেনে নিজে এই ইভিল সম্পর্কে কী ভাবেন, তাঁর উদ্দেশ্যই বা কি তার দার্শনিক উত্তর খুঁজতে চেয়েছেন সার্ত্রে ।
তৃতীয় পর্বে ফরাসি পাঠকদের কাছে বিস্ময়কর কিংবদন্তি হিসাবে দেখা দেন জেনে। তাঁর পাঠকেরা অবাক হয়ে গাঁটকাটা, পায়ুবিক্রেতা, চোর, স্কুল-পলাতক, গৃহ-পলাতক থেকে তাঁর লেখক সত্তার সঙ্গে পরিচিত হতে থাকেন । সমাজের স্বীকৃতি পাবার পরও জেনে ভবঘুরে, পায়ুবেশ্যা, সমকামী, চুরি ইত্যাদির সঙ্গে জড়িয়েছিলেন । তিনি বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন এবং আমেরিকার ‘ব্ল্যাক প্যান্হার’ ও প্যালেস্টাইনের স্বাধীনতা আন্দোলনের পক্ষে বক্তৃতা দেন ; ছবি তুলে তাইলেও মাঝখানের আঙুল তুলে ধরতেন । অবশ্য গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজকেও দেখা গেছে ফোটোগ্রাফারদের সামনে মধ্যমা তুলে ধরতে । যখন সমালোচকদের কাছে তিনি একজন প্রতিভাবান লেখক ও ভাবুক হিসাবে স্বীকৃতি পেলেন তখন জাঁ ককতো, সার্ত্রে প্রমুখ ফরাসি সাহিত্যিকদের উদ্যোগে যাবজ্জীবনের কারাদণ্ড থেকে মুক্তি পান ।
সার্ত্রে জেনেকে সন্ত বলেছেন তার কারণ জেনে নিজের পক্ষে যে নৈতিকতাবোধ গড়ে নিয়েছেন তা আদি-নিষ্কলুষতা ও সত্য তাড়িত এবং জেনে এই অবস্হান থেকে খ্রিস্টধর্মীর ‘নষ্ট নিষ্ঠা’ স্বীকার করছেন না । মানসিক স্হিরতা পাবার অভিপ্রায়ে তাঁর নৈতিকতাবোধ একটি দ্বিমেরু সাধনী । নিজের কাছে তিনি সৎ, কেননা নৈতিকতার সাদা-কালোকে তিনি যে কোনো ধরণের জঞ্জাল ও প্রতিপন্হী সামাজিক এঁটোকাঁটা থেকে তৈরি করে ফেলতে পারেন ; তাঁর কাছে তাই বাইবেল-পড়ুয়া গির্জা-বালক আর দক্ষ পেশাদার চোরের তফাত নেই । জেনে শয়তানি বা পাপ বা ইভিলের সততা থেকে ঝুঁকে পড়েন কালো নান্দনিকতায় ; এই মেটামরফোসিস তিনি নিজেও তখন হৃদয়ঙ্গম করেননি । তাঁর তখনও মনে হতো যে শয়তানির সূর্যালোকে থেকেও তিনি নতুন এক সূর্যালোক খুঁজে পেয়েছেন, যার নাম সৌন্দর্য । এই পর্বে সার্ত্রে শিল্প ও নান্দনিক নির্ণায়ক প্রতিষ্ঠার সঙ্গে জেনের আত্মআবিষ্কারকে গুরুত্ব দিয়েছেন ।
চতুর্থ পর্বে, সার্ত্রে যখন জেনের তৃতীয় মেটামরফোসিসের কথা বলছেন তখন জেনে একজন প্রতিভাবান লেখক । সার্ত্রে কিন্তু বলছেন যে জেনের উপন্যাসগুলো মেকি এবং তার গদ্যও মেকি। কিন্তু মেকি হোক বা নাহোক, তাদের উৎস হলো জ্ঞাপন করার সদিচ্ছা । জেনে কায়দা করে তাঁর পাঠকদের ব্যবহার করেছেন, তিনি তাদের ব্যবহার করেছেন নিজের বিষয়ে নিজের সঙ্গে কথোপকথনের উদ্দেশে । সার্ত্রে বলেছেন যে এই বিশেষত্ব পাঠকদের দূরে সরিয়ে দিতে পারে । কোনো আলোচকই অবশ্য জেনেকে দূরে সরিয়ে দিতে চাননি ; পাঠকরা বরং অবাক হয়ে প্রশংসা করেছে জেনের এই মেটামরফোসিসকে ।
১৯৬৪ সালে ‘প্লেবয়’ পত্রিকায় ম্যাডেলিন গোবিলকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে সার্ত্রে সম্পর্কে জেনে বলেছিলেন, “জগতে যখন সবাই শ্রদ্ধেয় বেশ্যা হতে চাইছে, তখন এরকম একজনের দেখা পেতে ভালো লাগে যে জানে যে সে একটু-আধটু ছেনাল কিন্তু শ্রদ্ধেয় হতে চায় না । সার্ত্রের বইটা সম্পর্কে ওই একই সাক্ষাৎকারে জেনে বলেছেন, যদিও তিনি পাণ্ডুলিপি পড়েছিলেন কিন্তু প্রকাশিত হবার পর বইটা তাঁকে নিদারুণ বিরক্তিতে আক্রান্ত করেছিল, কেননা অন্য একজন লোক তাঁকে উলঙ্গ করে দিয়েছিল ; যখন তিনি নিজেকে নগ্ন করেন তখন তিনি প্রয়াস করেন যাতে তাঁর ক্ষতি না হয় আর তা করার জন্য শব্দ, মনোভাব, বাদবিচার, ম্যাজিক ইত্যাদির মাধ্যমে ছদ্মবেশ ধরেন । পড়ে তাঁর তক্ষুনি মনে হয়েছিল বইটা পুড়িয়ে ফেলবেন ; বইটার চাপে কিছুদিনের জন্য তাঁর লেখালিখি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ; এক ধরণের শূন্যতা ও মানসিক অপকর্ষ সৃষ্টি করেছিল । তিনি যান্ত্রিকের মতন বহু উপন্যাস লিখে ফেলতে পারতেন, পর্নোগ্রাফিক বই লিখতে পারতেন, কিন্তু সার্ত্রের বই অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। ওই শূন্যতাবোধ কাটাবার জন্য তিনি নাটক লেখা আরম্ভ করেন। ”
পক্ষান্তরে বইতে সার্ত্রে জিগ্যেস করেছেন, “আমি কি জেনের প্রতি যথেষ্ট ন্যায্য থাকতে পেরেছি ?” সার্ত্রের দরুণ কিন্তু জেনের প্রচার বেড়ে যায় এবং তিনি ধনী হয়ে ওঠেন, প্রতিসংস্কৃতির প্রতিনিধি । যে সমাজ একসময়ে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছিল তাকে বিদ্রূপ করার সুযোগ কখনও ছাড়েননি । সার্ত্রে বলেছেন, জেনে আমাদের দিকে আয়না মেলে ধরেন ; আমাদের উচিত তাতে নিজেদের আসল চেহারা দেখা ।
জেনের বইগুলো আর সার্ত্রের বইটির আয়নায় নিজেদের দেখে পাঠকের নিজস্ব প্রতিভাস ও পরিজ্ঞান ঘটার কথা । সুসান সোনটাগ তাঁর ‘এগেইনস্ট ইনটারপ্রিটেশান অ্যাণ্ড আদার এসেজ’ গ্রণ্হে সার্ত্রের বইটিকে বলেছেন, “ক্যানসার, হাস্যকর বাগাড়ম্বরে ঠাশা, এর আলোকিত ধারণার মালপত্রকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় চটচটে গাম্ভীর্য আর বীভৎস পুনরাবৃত্তির স্বরভঙ্গী।” প্রকাশক গালিমার সার্ত্রেকে বলেছিল জেনের সাহিত্য সংগ্রহের একটা ভূমিকা লিখে দিতে আর সেটাই শেষ পর্যন্ত হয়ে দাঁড়ালো ৬০০ পাতার দানব । সার্ত্রের বইটা জীবনী নয়, সাহিত্য সমালোচনাও নয় । বইটা তাঁর অস্তিত্ববাদ বোঝাবার ময়দান । সোনটাগ বলেছেন, বই লিখতে বসে সার্ত্রে তাঁর বিষয় পেয়ে গেলেন, নিজে তো ডুবলেনই, জেনেকেও ডোবালেন । সোনটাগ বলেছেন যে পাঠক যদি সার্ত্রের দর্শনের সঙ্গে পরিচিত হন, তাহলে বইটার পাঠ সহায়ক হবে, অন্তত ভাসা-ভাসাভাবে। সার্ত্রেকে সঙ্গে নিয়ে পাঠক জেনে সম্পর্কে তাঁর কৌতূহল মেটাতে পারবেন । তবে সার্ত্রে এতো বেশি জেনে সম্পর্কে কথা বলেছেন যে শেষ পর্যন্ত জেনে আর জেনে থাকেন না ।
এডমাণ্ড হোয়াইট ১৯৯৩ সালে নথিপত্র দেখে গবেষণার পর জেনের যে জীবনী লিখেছিলেন তাতে বলেছেন যে শৈশব-তারুণ্যের যে ঘটনাগুলো জেনে লিখেছেন তার বেশির ভাগই কাল্পনিক ও অসত্য এবং তা জেনের ব্যক্তিগত কিংবদন্তি বানাবার দক্ষতা ; সার্ত্রে এগুলোকে যাচাই না করে জেনের বানানো গল্পের ওপর নির্ভর করে বইটা খাড়া করেছিলেন । সার্ত্রে ব্যক্তিগতভাবে জেনেকে জানতেন, এবং বইতে লিখেওছেন যে জেনে ইতিহাসকে তোয়াক্কা করে না আর কিংবদন্তি দিয়ে ফাঁকগুলো ভরে দেবে । আসলে ওই কিংবদন্তি সার্ত্রের জন্য জরুরি ছিল তাঁর বইয়ের বিষয়কে কেন্দ্র করে যাতে নিজস্ব নৈতিক আর দার্শনিক তত্বকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করতে পারেন ।
তাঁর গদ্যের মারপ্যাঁচ দিয়ে জেনে নিজেকে ল্যাঠামাছের মতন পিচ্ছিল করে তুলেছিলেন ; গড়ে তুলেছিলেন ছায়াময় একজন “আমি”, যার ঝলক তিনি পাঠকদের দিতে থাকেন । সার্ত্রে এই ঝলকটাকে বইয়ের পাতায় গিঁথে দিয়ে অস্তিত্ববাদী প্রপঞ্চবিজ্ঞানকে ছড়িয়ে দেবার সুযোগ ছাড়েননি । মূলাগত স্বাধীনতাবোধ এবং নির্নিমিত্ততা হলো তাঁর তর্কের বনেদ ; ফলে আত্ম-প্রতিস্ব গড়ার জন্য জেনের বানানো কাহিনি তাঁর কাজে লেগেছে । সার্ত্রে অবশ্য বলেছেন যে জেনের গদ্য মেকি বলে জেনে একজন স্বজ্ঞাত লেখকের সম্পূর্ণ বিপরীত, তাঁর নানন্দনিকতায় সৌন্দর্যকে দখল করা প্রচেষ্টা রয়েছে কিন্তু তাঁর আকাঙ্কা নেই সৌন্দর্যের প্রতি ; মেকি গদ্যের ফলে জেনে অন্ধকার জগতের মানুষের মতন শিল্পী হিসাবেও ফন্দিবাজ, ধড়িবাজ ; লেখায় বাগ্মীতা দেখাবার চেষ্টা বেশি এবং সন্ত্রাসের যথেষ্ট অভাব রয়েছে ।
‘প্লেবয়’ পত্রিকার ১৯৬৪ সালের সাক্ষাৎকারে ম্যাডেলিন গোবিল জেনেকে জিগ্যেস করেছিলেন, “আপনি চোর, বিশ্বাসঘাতক আর সমকামী হলেন কেন ?” উত্তরে জেনে বলেছিলেন, “আমি নিজে নির্ণয় নিইনি, আমি কোনও নির্ণয় নিইনি । কিন্তু কিছু তথ্যকে স্বীকার করতে হবে। আমি চুরি করতে আরম্ভ করললুম কেননা আমি ক্ষুধার্ত ছিলুম । সমকামিতার ক্ষেত্রে আমার কোনো ধারণা নেই। সমকামিতা আমার ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল, আমার চোখের রঙের মতন, আমার পায়ের সংখ্যার মতন। আকর্ষণটা সম্পর্কে অবগতির পর আমি নিজের সমকামিতাকে বেছে নিলাম, সার্ত্রের মতামত যা স্পষ্ট করেছে ।”
জেনের সমকামিতা সম্পর্কে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সার্ত্রে যা বলেছেন তা অনেকটা পরস্পরবিরোধী। সমকামিতার রহস্য, সার্ত্রে বলেছেন, জেনে তাকে অপরাধের গুরুত্ব দিয়েছেন, তা প্রকৃতিবিরোধী কেবল নয়, তা কাল্পনিকও । সমকামী মানুষ একজন অলস স্বপ্নদর্শী নয়, সে একজন প্রতারক, সে একজন ভণ্ড । জেনে বেছে নিয়েছেন নারীর ভূমিকা, আর তা করেছেন কেননা তিনি একজ রাজকুমার সাজতে চান, নকল রাজকুমার ।
সার্ত্রে সমকামবিরোধী ছিলেন না । সমকামবিরোধী হতে হলে ব্যাপারটাকে কল্পনার চেয়েও বেশি কিছু মনে করতে হবে । তাছাড়া, স্বাধীনতাবোধের যে দ্বান্দ্বিকতা সার্ত্রের দর্শন স্বীকার করে তার ভিত্তি হলো হেগেলের মালিক-গোলামের দ্বান্দ্বিকতা । সার্ত্রের আত্ম-প্রতিস্বের দর্শন ‘অপর’ সম্পর্কিত দর্শন থেকে আলাদা ও জটিল । ফেলিক্স গুত্তারি বলেছেন যে সার্ত্রের এই বক্তব্য রক্ষণশীল ; সার্ত্রের সমকামের জগতে পুরুষ নারী হিসাবে নিজেকে জাহির করে । সার্ত্রের মতে নারীরা পরস্পরের প্রতিবিম্ব, তারা পরস্পরকে স্বীকার করে না । নারীবাদী লেখিকা জুডিথ বাটলার এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে জেনের গদ্য, যা প্রধানত আত্মজীবনী ও ফিকশানের মিশ্রণ, তা হলে বহুরুপীর ছদ্মবেশী ভাষা, পুরুষের লিঙ্গবাদী লালিকা এবং নিটোল প্রতিস্ব গড়ে তোলার বদলে উল্টোবাঁক নিয়ে অস্হিতিশীল করার প্রয়াস । তাঁর ‘কুইয়ার রাইটিঙ : হোমোইরটিসিজম ইন জেনেজ ফিকশান’ বইতে আরও স্পষ্ট করে বলেছেন এলিজাবেথ স্টিফেন্স । তিনি বলেছেন, জেনের উপন্যাসগুলোতে গদ্যের ব্যবহার করা হয়েছে সংহতিনাশ ও পরাভূত করার কার্যপদ্ধতি হিসাবে, যে পদ্ধতি প্রয়োগ করে প্রথাগত ন্যারেটিভ আদলকে জেনে পালটে দিয়েছেন তাঁর উদ্ভট চরিত্রদের বিকৃত প্রভাব বর্ণনা করার খাতিরে । জেনের গদ্যে জেনে লোকটাকে সর্বত্র দেখা যায় কিন্তু লেখক জেনে মনে হয় মৃত, মাঝেমধ্যে ভুত হয়ে শব্দের ভেতরে উঁকি মারে । এই কারণেই জেনের বইগুলো পরস্পরবিরোধী ভাবনার পাঠকদের টাকে ; কারোর কাছে তিনি বৈপ্লবিক আবার কারোর কাছে প্রতিক্রিয়াশীল, সমকামিপ্রিয় এবং সমকামিভীত, পতিত এবং ফুলবাবু।
সার্ত্রের স্তরের একজন লেখক-দার্শনিক যে পরিশ্রম করেছেন তাঁর সময়ের একজন অবহেলিত লেখকের জন্য তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় । বড়ো খ্যাতিমান লেখকরা সাধারণত তরুণ ও কম খ্যাতির লেখকদের নিয়ে লেখেন না । আর এই বই তো একজন অপরাধীর বই ও ভাবনাচিন্তা নিয়ে । সার্ত্রে বলেছেন, জেনে আতঙ্ক সৃষ্টি করেন, কেননা জেনে চান তাঁকে ভালোবাসা হোক ; জেনের অসাধারণ বইগুলো নিজেরাই নিজেদের খণ্ডন করে । পুরুষালী সৌন্দর্যের তরুণদের সঙ্গে ভালোবাসাবাসি নিয়ে জেনের রয়েছে ফেটিশ এবং একধরণের ত্রাস ; তিনি বুঝে উঠতে পারেন না তাদের নিয়ে কি করা দরকার । জেনের বইগুলো পড়ার পর কিংবা পাশাপাশি তাঁর বই আর সার্ত্রের বই পড়লে পাঠক এই দুজনকেই গভীরভাবে জানতে পারবেন।
জাঁ জেনে নিঃসন্দেহে একটি চিত্তাকর্ষক জীবন কাটিয়েছিলেন, ককতো, জিয়াকোমেত্তি, গিন্সবার্গ, ইয়াসের আরাফাত, সার্ত্রের মতন বন্ধুবান্ধব, ব্ল্যাক প্যান্হার আর প্যালেস্টিনিয়দের প্রতি সমর্থন, ভীষণভাবে দেশাত্মবোধশূন্য, প্রচণ্ড প্রতিষ্ঠানবিরোধী, বারো বছর বয়সে স্কুল ছাড়া সত্বেও এবং সংশোধনাগার ও কারাগারে যৌবন কাটিয়েও, অবিশ্বাস্যরূপে শিক্ষিত। ১৯৪৩ সালে লেখা জেনের প্রথম বই ‘আওয়ার লেডি অব দি ফআওয়ার্স’কে অসাধারণ ফিকশান বলেছেন বিভিন্ন আলোচক ; কারাগার কর্তৃপক্ষ তাঁর প্রথম পাণ্ডুলিপি ছিঁড়ে ফেলা সত্বেও জেনে আবার স্মৃতি থেকে লিখতে পেরেছিলেন একই বই, কারাগারে বসে, তার কারণ ‘আওয়ার লেডি অব দি ফ্লাওয়ার্স’ প্রধানত জেনের অতীত আর তখনকার বর্তমানের অতিকথামূলক সৃষ্টি । স্মৃতির সঙ্গে তথ্য, কল্পনা, অযৌক্তিক স্বপ্ন, ভাবনাচিন্তা, অনুমান, দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টি, স্নেহপূর্ণ অনুভূতি, সহমর্মিতা মিশিয়ে তিনি তাঁর বিচ্ছিন্নতাকে যাতে সহনযোগ্য করে তুলতে পারেন তাই জেনে নিজের গড়া জগতে জগতে প্রবেশ করেছেন বইটার মাধ্যমে এবং এই জগতটিতে অন্য কেউই হস্তক্ষেপ করতে পারবে না, সে বিষয়ে তিনি নিশ্চিত ছিলেন । এখান থেকেই তাঁর জগতের বিস্তারের আরম্ভ ।
১৯৭০ সাল থেকে জেনে দু’বছর জর্ডনে প্যালেস্টিনীয়দের উদ্বাস্তু ক্যাম্পে কাটিয়েছিলেন, এবং তখনকার অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখেন ‘প্রিজনার অব লাভ’ । তিনি নিজেই একজন পরিত্যক্ত ব্রাত্য মানুষ, স্বাভাবিকভাবেই আকর্ষিত হয়েছিলেন বাস্তুচ্যূত জনগণের প্রতি, এমনই এক আকর্ষণ যা তাঁর কাছে জটিল আর কালসহ হয়ে দেখা দিয়েছিল । ১৯৮৬ সালে যখন তিনি বইটি লিখছেন তখন তাঁর পরিচিতজনদের অনেকে মারা গেছেন, জেনে নিজেও মৃত্যুর কাছাকাছি, কিন্তু এই বইতে অন্ধকারজগতের লোকটি নেই ; যিনি আছেন তিনি ইহুদি-বিরোধী একজন লেখক, কেবল প্যালেস্টিনীয় উথ্থানকে সমর্থন করছেন না, তিনি বিপ্লবকে সমর্থন করছেন, সরল গদ্যে, খোলাখুলি রাজনৈতিক মতামত ব্যক্ত করছেন, বিশ্লেষণ করছেন দৃশ্যাবলীর রাজনীতি এবং আত্মপরিচয়ের সন্মোহিনী ও অননুগত বৈশিষ্ট্য । তাঁর এই শেষ বইটি, বর্তমান উপদ্রুত পৃথিবীর সবচেয়ে রক্তাক্ত দ্রোহ, নিপীড়ন ও সন্ত্রাসবেষ্টিত বধ্যভূমির উদ্দেশে একটি কাব্যিক ও দার্শনিক যাত্রা ।
 মলয় রায়চৌধুরী | 27.58.255.50 | ১০ আগস্ট ২০২১ ১৯:২৩734846
মলয় রায়চৌধুরী | 27.58.255.50 | ১০ আগস্ট ২০২১ ১৯:২৩734846ট্রাউজার-পরা মেঘ : ভ্লাদিমির মায়াকভস্কি
অনুবাদ : মলয় রায়চৌধুরী
প্রস্তাবনা
তুমি ভাবলে,
স্যাঁতসেতে এক মগজের কল্পনায়,
এক তেলচিটে খাটে হাত-পা-ছড়ানো পেট-মোটা চাকরের মতন,--
আমার হৃদয়ের রক্তাক্ত ছেঁড়া টুকরো নিয়ে, আমি আবার ঠাট্টা করব ।
যতক্ষণ না আমি উপেক্ষিত নই, আমি হবো নিষ্ঠুর আর পীড়াদায়ক ।
আমার চিত্তে আর দাদুসুলভ স্নেহশীলতা নেই,
আমার আত্মায় আর ধূসর চুল নেই !
আমার কন্ঠস্বর দিয়ে জগতকে ঝাঁকিয়ে আর কাষ্ঠহাসি হেসে,
আমি তোমাদের পাশ দিয়ে চলে যাই, -- সৌম্যকান্তি,
বাইশ বছর বয়সী ।
সুশীল ভদ্রমহোদয়গণ !
তোমরা বেহালায় তোমাদের ভালোবাসা বাজাও ।
অমার্জিতরা তা ঢোলোকে তারস্বরে বাজায় ।
কিন্তু তোমরা কি নিজেদের অন্তরজগতকে বাইরে আনতে পারো, আমার মতন
আর কেবল দুটো ঠোঁট হয়ে যেতে পারো পুরোপুরি ?
এসো আর শেখো--
তোমরা, দেবদূত-বাহিনীর ফুলবাবু আমলার দল !
মিহি কাপড়ের বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে এসো
আর তোমরা, যারা তোমাদের ঠোঁট পেতে দিতে পারো
সেই রাঁধুনীর মতন যে নিজের রান্নার বইয়ের পাতা ওলটায় ।
যদি তোমরা চাও--
আমি কাঁচা মাংসের ওপরে চারুশিল্পের শত্রুর মতন লালসিত হবো
কিংবা সূর্যোদয় যে উদ্রেক ঘটায় তার রঙে পালটে দেবো,
যদি তোমরা চাও---
আমি হতে পারি অনিন্দনীয় সুশীল,
মানুষ নয় -- কিন্তু ট্রাউজার-পরা এক মেঘ।
আমি সুন্দর অঙ্কুরোদ্গমে বিশ্বাসকে প্রত্যাখ্যান করি !
তা সত্ত্বেও আমি তোমাদের প্রশংসা করব, ---
পুরুষের দল, হাসপাতালের বিছানার চাদরের মতন কোঁচকানো,
আর নারীরা, অতিব্যবহৃত প্রবাদের মতন নির্যাতিত ।
প্রথম পর্ব
তোমরা কি ভাবছ আমি ম্যালেরিয়ায় ভুল বকছি ?
তা ঘটেছিল ।
ওডেসায়, তা ঘটেছিল ।
“আমি চারটের সময় আসব,” কথা দিয়েছিল মারিয়া ।
আটটা…
নয়টা…
দশটা…
তারপর তাড়াতাড়ি,
সন্ধ্যা,
বিরাগ দেখানো,
আর ডিসেম্বরসুলভ,
জানালাগুলো ছেড়ে
আর ঘন অন্ধকারে মিলিয়ে গেল ।
আমার পেছন থেকে, আমি শুনতে পাই হ্রেষা আর হাসি
ঝাড়বাতিগুলোর ।
তোমরা আমায় চিনতে পারতে না যদি আগে থেকে পরিচিত হতে :
পেশীতন্তুর স্তুপ
গোঙানি,
স্নায়বিক অস্হিরতা ।
এরকম একজন বোকাটে কি চাইতে পারে ?
কিন্তু একজন বোকাটে অনেক কিছু চায় ।
কেননা নিজের জন্য তা অর্থহীন
তা তোমরা তামায় গড়া হও
কিংবা হৃদয় হোক শীতল ধাতুর ।
রাতের বেলায়, তোমাদের দাবিকে জড়িয়ে নিতে চাইবে
মেয়েলি কোনোকিছু দিয়ে,
কোমল ।
আর এইভাবে,
বিশাল,
আমি কাঠামোর ভেতরে প্রতিষ্ঠিত হই.
আর আমার কপাল দিয়ে, গলিয়ে ফেলি জানালার কাচ ।
এই ভালোবাসা কি অসাধারণ হবে নাকি গতানুগতিক ?
তা কি বজায় থাকবে নাকি উপেক্ষিত হবে ?
বিরাট কেউ এরকম দেহে আঁটবে না :
একটু ভালোবাসা জরুরি, -- একটা শিশু, হয়তো,
যখন মোটরগাড়ি হর্ন বাজায় আর আওয়াজ করে তখন এ ভয় পায়,
কিন্তু ঘোড়ায়-টানা ট্র্যামের ঘণ্টি পছন্দ করে ।
আমি মুখোমুখি হলুম
তরঙ্গায়িত বৃষ্টির সঙ্গে,
তবু আরেকবার,
আচ্ছা অপেক্ষা করো
শহুরে ফেনার বজ্রপাতের গর্জনে ভিজে গেলুম ।
ছুরি নিয়ে পাগলের মতন বাইরে বেরিয়ে,
রাত ওকে ধরে ফেললো
আর ছুরি মেরে দিলো,
কেউ দেখেনি ।
ঠিক মধ্যরাতে
গিলোটিন থেকে খসা মুণ্ডুর মতন পড়ে গেলো।
জানালার কাচে রুপোর বৃষ্টিফোঁটা
জমিয়ে তুলছিল মুখবিকৃতি
আর চেঁচাচ্ছিল ।
যেন নত্রে দামের পশুমুখো নর্দমাগুলো
চেল্লানো আরম্ভ করে দিলো ।
ধিক্কার তোমাদের !
যা ঘটেছে তাতে কি তোমরা এখনও সন্তুষ্ট নও ?
কান্না এবার চারিধার থেকে আমার গলা কাটবে।
আমি শুনতে পেলুম:
আস্তে,
বিছানার বাইরে রোগীর মতন,
একটা স্নায়ু লাফালো
নীচে ।
প্রথমে,
পুরুষটা সরে যায়নি, প্রায় ।
তারপর, সন্দিগ্ধ
আর সুস্পষ্ট,
ও লাফাতে আরম্ভ করলো।
আর এখন, ও আর আরও দুই জন,
এদিক-ওদিক লাফাতে লাগলো, তিড়িঙ নাচ ।
একতলায়, পলেস্তারা তাড়াতাড়ি খসে পড়ছিল ।
স্নায়ুরা,
বড়োগুলো
ছোটোগুলো,--
নানান ! --
পাগলের মতন টগবগাতে আরম্ভ করলো
যতক্ষণ না, শেষে,
ওদের পা ওদের টানতে অক্ষম হলো ।
ঘর থেকে রাত টপটপ করে বেরিয়ে এলো আর ডুবে গেলো।
চটচটে মাটিতে আটকে গিয়ে, চোখ তা থেকে পিছলে বের করতে পারলো না।
হঠাৎ দরোজাগুলো দুমদাম করতে লাগলো
যেন হোটেলের দাঁতগুলো কিড়মিড় করতে শুরু করেছে ।
তুমি প্রবেশ করলে,
আচমকা যেন “এই নাও !”
সোয়েড চামড়ার মোচড়ানো দস্তানা পরে, তুমি অপেক্ষা করলে,
আর বললে,
“তুমি জানো,--
আমার শিগগির বিয়ে হবে।”
তাহলে যাও বিয়ে করো ।
ঠিকই আছে,
আমি সামলে নিতে পারবো ।
দেখতেই পাচ্ছো -- আমি শান্ত, নিঃসন্দেহে !
কোনো শবের
নাড়ির স্পন্দনের মতন ।
মনে আছে ?
তুমি বলতে :
“জ্যাক লণ্ডন,
টাকাকড়ি,
ভালোবাসা আর আকুলতা,”--
আমি কেবল একটা ব্যাপারই দেখেছি :
তুমি ছিলে মোনালিসা,
যাকে চুরি করা জরুরি ছিল !
আর কেউ তোমায় চুরি করে নিলো ।
ভালোবাসায় আবার, আমি জুয়া খেলা আরম্ভ করব,
আমার ভ্রুর তোরণ আগুনে উদ্ভাসিত ।
আর কেনই বা নয় ?
অনেক সময়ে গৃহহীন ভবঘুরেরা
পোড়া বাড়িতেও আশ্রয় খোঁজে !
তুমি আমাকে ঠাট্টা করছো ?
“উন্মাদনার কেবল গুটিকয় চুনী আছে তোমার
ভিখারির কয়েক পয়সার তুলনায়, একে ভুল প্রমাণ করা যাবে না !”
কিন্তু মনে রেখো
এইভাবেই পম্পেইয়ের শেষ হয়েছিল
যখন কেউ ভিসুভিয়াসের সঙ্গে ইয়ার্কি করেছিল !
ওহে !
ভদ্রমহোদয়গণ !
তোমরা অশুচি
নিয়ে চিন্তা করো,
অপরাধ
আর যুদ্ধ ।
কিন্তু তোমরা কি দেখেছো
ভয়ঙ্কর সন্ত্রস্ত
আমার মুখ
যখন
তা
নিখুঁত শান্তিময়তায় থাকে ?
আর আমি অনুভব করি
“আমি”
আমাকে ধরে রাখার জন্য খুবই ক্ষুদ্র ।
আমার অন্তরে কেউ কন্ঠরুদ্ধ হচ্ছে ।
হ্যালো !
কে কথা বলছে ?
মা ?
মা !
তোমার ছেলের হয়েছে এক অত্যাশ্চর্য অসুখ !
মা !
ওর হৃদয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়েছে !
তার বোন, লিডিয়া আর ওলগাকে বোলো
যে আর কোথাও কোনো লুকোবার জায়গা নেই ।
প্রতিটি শব্দ,
মজার হোক বা অভদ্র,
যা ও নিজের জ্বলন্ত মুখ থেকে ওগরায়,
উলঙ্গ বেশ্যার মতন ঝাঁপিয়ে পড়ে
জ্বলন্ত বেশ্যালয় থেকে ।
লোকেরা গন্ধ শোঁকে--
কোনো কিছু পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে ।
ওরা দমকলকে ডাকে ।
ঝলমলে হেলমেট পরে
তারা অবহেলাভরে ভেতরে প্রবেশ করতে থাকে ।
ওহে, দমকলের লোকদের বলো :
বুটজুতো পরে ঢোকার অনুমতি নেই !
গনগনে হৃদয় নিয়ে একজনকে বিচক্ষণ হতে হবে ।
আমিই তা করব !
আমি আমার জলভরা চোখ ঢেলে দেবো চৌবাচ্চায় ।
আমাকে কেবল আমার পাঁজরকে ঠেলতে দাও আর আমি আরম্ভ করে দেবো।
আমি লাফিয়ে পড়বো ! তোমরা আমাকে বাধা দিতে পারবে না !
তারা বিদ্ধস্ত ।
তোমরা হৃদয় থেকে লাফিয়ে পড়তে পারবে না !
ঠোঁটের ফাটল থেকে,
এক অঙ্গার-আস্তৃত চুমু উৎসারিত হয়,
জ্বলন্ত মুখাবয়ব থেকে পালিয়ে যায় ।
মা !
আমি গান গাইতে পারি না ।
হৃদয়ের প্রার্থনাঘরে, আগুন লাগিয়ে দেয়া হয়েছিল গায়কদের গায়ে !
শব্দাবলী আর সংখ্যাসমূহের প্রতিমাদের
খুলির ভেতর থেকে,
জ্বলন্ত বাড়ি থেকে শিশুদের মতন, পালাতে থাকে ।
এইভাবে ভয়,
আকাশে পৌঁছে, ডাক দেয়
আর তুলে ধরে
লুসিতানিয়ার আগুনে-বাহু আর উদ্বেগ ।
শত-চোখ আগুন শান্তির দিকে তাকালো
ফ্ল্যাটবাড়ির দিকে, যেখানে লোকেরা ঘামছিল ।
এক শেষতম চিৎকারে,
তুমি কি গোঙাবে, অন্তত,
শতাব্দীগুলোকে প্রতিবেদন দেবার জন্য যে আমি অগ্নিদগ্ধ ?
দ্বিতীয় পর্ব
আমার মহিমাকীর্তন করো !
প্রসিদ্ধরা কেউ আমার সমকক্ষ নয় !
যাকিছু এপর্যন্ত করা হয়েছে তার ওপরে
আমি ছাপ মেরে দিই “নস্যাৎ।”
আপাতত, আমার পড়ার ইচ্ছে নেই।
উপন্যাস ?
তাতে কি !
বইপত্র এইভাবে তৈরি হয়,
আমি ভাবতুম :--
একজন কবির আগমন হয়,
আর নিজের ঠোঁট অনায়াসে খোলে।
অনুপ্রাণিত, মূর্খটা বেমালুম গাইতে আরম্ভ করে--
ওহ ক্ষান্তি দাও !
দেখা গেলো :
উৎসাহে গাইবার আগে,
নিজেদের কড়া-পড়া পায়ে ওরা কিছুক্ষণ তাল ঠোকে,
যখন কিনা কল্পনার ঘিলুহীন মাছেরা
হৃদয়ের পাঁকে কাদা ছেটায় আর মাখামাখি করে ।
আর যখন, ছন্দে হিসহিসোচ্ছে, ওরা গরম জলে সেদ্ধ করে
যাবতীয় ভালোবাসা আর পাপিয়া-পাখিদের ক্বাথের মতন ঝোলে,
জিভহীন পথ কেবল কিলবিল করে আর কুণ্ডলী পাকায়---
তাতে আর্তনাদ করার বা এমনকি বলার মতো কিছুই থাকে না ।
আমরা নিজের গর্ববশে, সারাদিন সৎমেজাজে কাজ করি
আর ব্যাবেলের শহর-মিনারগুলোর আবার পুনরানয়ন হয় ।
কিন্তু ঈশ্বর
গুঁড়িয়ে
এই শহরগুলোকে ফাঁকা মাঠে পালটে ফ্যালেন,
শব্দকে মন্হন করে ।
নৈঃশব্দে, রাস্তাকে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হয় দুর্দশায়।
গ্রাসনলিকার পথে এক চিৎকার ঋজু দাঁড়িয়ে পড়ে।
যখন মোটাসোটা ট্যাক্সি আর মোটরগাড়ি অন্তরায়ে স্হির,
গলার ভেতরে আটকে থাকে ।
যেন ক্ষয়রোগের কারণে,
নিষ্পিষ্ট বুক শ্বাস নেবার জন্য খাবি খাচ্ছিল ।
শহর, বিষাদে আক্রান্ত, তাড়াতাড়ি রাস্তা বন্ধ করে দিলো ।
আর তখন--
তা সত্ত্বেও !--
রাস্তাটা চৌমাথার মোড়ে নিজের ধকল উগরে দিলো কেশে
আর গলা থেকে বারান্দাকে ঠেলে বের করে দিলো, শেষ পর্যন্ত,
মনে হলো যেন,
শ্রেষ্ঠশ্রেনির দেবদূতের গায়কদলের ধুয়ায় যোগ দিয়ে,
সাম্প্রতিককালে লুন্ঠিত, ঈশ্বর তার তাপ আমাদের দেখাবে !
কিন্তু রাস্তাটা উবু হয়ে বসে কর্কশকন্ঠে চেঁচিয়ে উঠলো :
“খেতে যেতে দাও !”
শিল্পপতি ক্রুপ আর তার আণ্ডাবাচ্চারা ঘিরে ধরে
শহরে চোখরাঙানো ভ্রু আঁকার জন্য,
যখন কিনা সঙ্কীর্ণ প্রবেশপথে
শব্দাবলীর লাশ এদিক-ওদিক ছড়ানো পড়ে থাকে,--
দুটো বেঁচে থাকে আর মাথাচাড়া দ্যায়,--
“শুয়োর”
আর অন্যটা,--
আমার মনে হয় “খাবার সুপ” ।
আর কবির দল, ফোঁপানি আর নালিশে ভিজে সপসপে,
রাস্তা থেকে দৌড় লাগায়, বিরক্ত আর খিটখিটে :
“ওই দুটো শব্দ দিয়ে এখন আর ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়
এক সুন্দরী রমণী
কিংবা ভালোবাসা
কিংবা শিশির-ঢাকা ফুল।”
আর কবিদের পর,
অন্যান্য হাজার লোকের হুড়োহুড়ি আরম্ভ হলো :
ছাত্রছাত্রীর দল,
বেশ্যার দল,
বিক্রেতার দল ।
ভদ্রমহোদয়গণ,
থামুন !
আপনারা তো অভাবগ্রস্ত নন ;
তাহলে ভদ্রমহোদয়গণ কেন আপনারা ওগুলো চাইছেন !
প্রতিটি পদক্ষেপে দালান অতিক্রম করে,
আমরা স্বাস্হ্যবান আর অত্যুৎসাহী !
ওদের কথা শুনবেন না, বরং ওদের পিটুনি দিন !
ওদের,
যারা মাঙনার বাড়তি হিসাবে সেঁটে রয়েছে
প্রতিটি রাজন্য-বিছানায় !
আমাদের কি নম্রভাবে ওদের জিগ্যেস করতে হবে :
“সাহায্য করো, দয়া করে !”
স্তবগানের জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করতে হবে
আর বাগ্মীতার জন্য ?
আমরা জ্বলন্ত স্তবগানের সৃষ্টিকারী
কলমিল আর রসায়ানাগারের গুনগুনানির পাশাপাশি ।
আমি কেন ফাউস্তের কথা ভাবতে যাবো ?
আতশবাজির লুন্ঠনে পরীদের প্রদর্শন করে
ও মেফিসটোফিলিসের সঙ্গে নক্ষত্রপূঞ্জের নকশাকাটা পাটাতনে পিছলে চলেছে !
আমি জানি --
আমার বুটজুতোয় একটা পেরেক
গ্যেটের কল্পনার চেয়ে বেশি ভয়াবহ !
আমি
সবচেয়ে সোনালী-হাঁমুখের
প্রতিটি শব্দের সঙ্গে আমি দিচ্ছি
দেহের এক নামদিবস,
আর আত্মাকে এক পূনর্জন্ম,
আমি তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি :
জীবজগতের কণাও
আমি এই পৃথিবীতে যা কিছু করব তার চেয়ে অনেক বেশি !
শোনো !
বর্তমান যুগের জরাথুষ্ট্র,
ঘামে ভিজে,
তোমাদের চারিপাশে দৌড়োচ্ছে আর এখানে ধর্মপ্রচার করছে ।
আমরা,
বিছানার কোঁচকানো চাদরের মতন মুখ নিয়ে,
ঝাড়লন্ঠনের মতন ঝোলা ঠোঁটে,
আমরা,
কুষ্ঠরোগীর জন্য নির্দিষ্ট শহরে বন্দী,
যেখানে, জঞ্জাল আর সোনা থেকে, কুষ্ঠরোগীদের ঘা দেখা দিয়েছিল,
আমরা ভেনিসের নীলাভ সমুদ্রের চেয়ে পবিত্র,
রোদ্দুরের মলম-রশ্মিতে ধোয়া ।
আমি সেই তথ্যে থুতু ফেলি
যে হোমার আর ওভিদ সৃষ্টি করেননি
গুটিবসন্তে ঢাকা ঝুল,
আমাদের মতন সব মানুষদের,
কিন্তু সেই সঙ্গে, আমি জানি যে
সূর্য ফ্যাকাশে হয়ে যাবে
যদি তা আমাদের আত্মার সোনালি খেতের দিকে তাকায়।
প্রার্থনার তুলনায় পেশী আমাদের কাছে নির্বিকল্প !
আমরা আর ভরতুকির জন্য প্রার্থনা করব না !
আমরা--
আমরা প্রত্যেকে--
নিজেদের মুঠোয় ধরে রাখি
জগতকে চালনা করার লাগাম !
এ-থেকেই সভাস্হলগুলোয় গোলগোথার সূত্রপাত
পেট্রোগ্রাড, মসকো, কিয়েভ, ওডেসায়,
আর তোমাদের একজনও সেখানে ছিলে না যারা
এইভাবে হাঁক পাড়ছিল না :
“ওকে ক্রুসবিদ্ধ করো !
ওকে উচিত শিক্ষা দাও !”
কিন্তু আমার কাছে,--
জনগণ,
এমনকি তোমরা যারা জঘন্য ব্যবহার করেছ,--
আমার কাছে, তোমরা প্রিয় আর আমি গভীরভাবে তোমাদের কদর করি।
দেখোনি কি
যে হাত তাকে পেটাচ্ছে সেই হাতকেই কুকুরটা চাটছে ?
আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করে
আজকালকার দলবল ।
তারা তৈরি করেছে
আমাকে নিয়ে
একটা নোংরা পরিহাস ।
কিন্তু আমি সময়ের পাহাড়কে ডিঙিয়ে দেখতে পাই,
ওনাকে, যাঁকে কেউ দেখতে পায় না ।
যেখানে মানুষের দৃষ্টিশক্তি পৌঁছোয় না,
বিপ্লবের কাঁটার মুকুট পরে,
ক্ষুধার্ত মানুষদের নেতৃত্ব দিয়ে,
১৯১৬ সাল ফিরে আসছে ।
তোমাদের মধ্যে, ওনার অগ্রদূত,
যেখানেই দুঃখকষ্ট থাকবে, আমি থাকবো কাছাকাছি ।
আমি সেখানে নিজেকে ক্রুশবিদ্ধ করেছি,
প্রতিটি অশ্রুফোঁটার ওপরে ।
ক্ষমা করার মতন এখন আর কিছু নেই !
যে আত্মারা সমবেদনার অঙ্কুরের জন্ম দেয়, আমি পুড়িয়ে দিয়েছি তার ক্ষেত ।
তা অনেক কঠিন
হাজার হাজার ব্যাষ্টিল আক্রমণের তুলনায় ।
আর যখন
তাঁর আবির্ভাব ঘোষিত হয়,
আনন্দে আর গর্বে,
তোমরা এগিয়ে যাবে উদ্ধারককে অভ্যর্থনা জানাতে--
আমি টেনে নিয়ে যাবে
বাইরে আমার আত্মাকে,
আর পায়ে পিষবো
যতক্ষণ না তা ছড়িয়ে পড়ছে !
আর তোমাদের হাতে তুলে দেবো, রক্তে লাল, পতাকা হিসাবে ।
তৃতীয় পর্ব
আহ, কেমন করে আর কোথা থেকে
ব্যাপারটা এই পরিণতিতে পৌঁছেছে যে
উন্মাদনার নোংরা মুঠোগুলো
আলোকময় আনন্দের বিরুদ্ধে বাতাসে তুলে ধরা হয়েছিল ?
মেয়েটি এলো,--
পাগলাগারদের চিন্তায়
আর আমার মাথা ঢেকে দিলো বিষণ্ণতায় ।
আর যেমন ড্রেডনট যুদ্ধজাহাজের ধ্বংসের বেলায়
কন্ঠরুদ্ধ অঙ্গবিক্ষেপে
সেনারা আধখোলা দরোজার ভেতরে লাফিয়ে পড়েছিল, জাহাজডুবির আগে,
ভবিষ্যবাদী কবি বারলিয়ুক হামাগুড়ি দিয়ে এগোল, পেরিয়ে গেল
তাঁর চোখের চিৎকাররত ফাঁক দিয়ে ।
তাঁর চোখের পাতাকে প্রায় রক্তাক্ত করে,
উনি দেখা দিলেন হাঁটু গেড়ে,
উঠে দাঁড়ালেন আর হাঁটতে লাগলেন
আর উত্তেজিত মেজাজে,
কোমলভাবে, অমন মোটা একজনের কাছে অপ্রত্যাশিত,
উনি কেবল বললেন :
“ভালো !”
ব্যাপারটা ভালোই যখন পর্যবেক্ষণে এক হলুদ সোয়েটার
আত্মাকে লুকিয়ে রাখে !
ব্যাপারটা ভালোই যখন
ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে, আতঙ্কের মুখোমুখি,
তুমি চেঁচিয়ে বলো :
“কোকো খাও -- ভ্যান হুটেন কোম্পানির !”
এই মুহূর্ত,
বাংলার আলোর মতন,
বিস্ফোরণে ঝলসে,
আমি কিছুর সঙ্গেই অদলবদল করব না,
কোনো টাকাকড়ির জন্যও নয় ।
চুরুটের ধোঁয়ায় মেঘাচ্ছন্ন,
আর মদের গেলাসের মতন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত,
যে কেউ কবি সেভেরিয়ানিন-এর মতো মাতাল-মুখো হতে পারে ।
কোন সাহসে তুমি নিজেকে কবি বলো
আর ধূসর, তিতির-পাখির মতন, নিজের আত্মাকে কিচিরমিচিরে ডুবিয়ে দাও !
তখন
পেতলের বাঘনখ দিয়ে
ঠিক এই মুহূর্তে
জগতের খুলিকে তোমায় চিরে ফেলতে হবে !
তুমি,
মাথায় শুধু একটিমাত্র ভাবনা নিয়ে,
“আমি কি শৈলী অনুযায়ী নাচছি ?”
দ্যাখো আমি কতো আনন্দিত
তার বদলে,
আমি,--
সদাসর্বদা একজন ভেড়ুয়া আর জোচ্চোর ।
তোমাদের সবার কাছ থেকে,
যারা মামুলি মজার জন্য ভালোবাসায় ভিজেছো,
যারা ছিটিয়েছো
শতকগুলোতে অশ্রুজল, যখন তোমরা কাঁদছিলে,
আমি বেরিয়ে চলে যাবো
আর সূর্যের একচোখ চশমাকে বসাবো
আমার বড়ো করে খোলা, একদৃষ্ট চোখে ।
আমি রঙিন পোশাক পরব, সবচেয়ে অস্বাভাবিক
আর পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াবো
জনগণকে খুশি দিতে আর তাতিয়ে তুলতে,
আর আমার সামনে
এক ধাতব দড়িতে গলাবাঁধা,
ছোটো কুকুরবাচ্চার মতন দৌড়োবে নেপোলিয়ান ।
একজন নারীর মতন, শিহরিত, পৃথিবী শুয়ে পড়বে,
আত্মসমর্পণ করতে চেয়ে, মেয়েটি ধীরে-ধীরে অবনত হবে ।
জীবন্ত হয়ে উঠবে সবকিছু
আর চারিদিক থেকে,
ওদের ঠোঁট তোতলা কথা বলবে :
“য়াম-য়াম-য়াম-য়াম !”
হঠাৎ,
মেঘের দল
আর বাতাসে অন্যান্য ব্যাপার
আশ্চর্য কোনো উত্তেজনায় আলোড়িত,
যেন শাদা-পোশাকে শ্রমিকদল, ওপরে ওইখানে,
হরতাল ঘোষণা করেছে, সবাই তিক্ত আর আবেগে আক্রান্ত ।
বর্বর বজ্র মেঘের ফাটল থেকে উঁকি দিলো, ক্রুদ্ধ ।
নাকের বিশাল ফুটো থেকে ঘোড়ার ডাক দিয়ে, গর্জন করলো
আর এক মুহূর্তের জন্যে, আকাশের মুখ তেবড়ে বেঁকে গেলো,
লৌহ বিসমার্কের ভেঙচির মতন ।
আর কেউ একজন,
মেঘের গোলকধাঁধায় জড়িয়ে,
কফিপানের রেস্তরাঁর দিকে, হাত বাড়িয়ে দিলো এখন :
দুটিই, কোমলতর,
আর নারীমুখ নিয়ে
আর একই সঙ্গে, কামান দাগার মতন ।
তুমি কি ভাবছো
ওটা চিলেকোঠার ওপরে সূর্য
কফিপানের রেস্তরারাঁকে আলতো আদর করতে চাইছে ?
না, আবার এগিয়ে আসছে সংস্কারকামীদের কচুকাটা করতে
উনি জেনেরাল গালিফেৎ !
ভবঘুরের দল, পকেট থেকে হাত বের করে নাও--
বোমা তুলে নাও, ছুরি কিংবা একটা পাথর
আর কেউ যদি লক্ষ্যের উদ্দেশ্যে ছুঁড়তে না পারে
তাহলে সে চলে আসুক কেবল নিজের কপাল দিয়ে লড়তে !
এগিয়ে যাও, ক্ষুধার্ত,
গোলামের দল,
আর নির্যাতিতরা,
এই মাছি ভনভনে জঞ্জালে, পোচো না !
এগিয়ে যাও !
আমরা সোমবারগুলো আর মঙ্গলবারগুলোকে
ছুটির দিনে পালটে দেবো, তাদের রাঙিয়ে দেবো রক্তে !
পৃথিবীকে মনে করিয়া দাও তাকে আমি হীন প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিলুম !
রূঢ় হও !
পৃথিবী
রক্ষিতার মুখের মতন ফুলে উঠেছে,
যাকে রথসচাইল্ড বেশি-বেশি ভালোবেসেছিল !
গুলির আগুনের বরাবর পতাকাগুলো উড়ুক
যেমন ওরা ছুটির দিনে করে, জাঁকজমকসহ !
ওহে, রাস্তার লন্ঠনেরা, পণ্যজীবীদের আরও ওপরে তোলো,
ওদের মড়াগুলোকে হাওয়ায় ঝুলতে দাও ।
আমি অভিশাপ দিলুম,
ছুরি মারলুম
আর মুখে ঘুষি মারলুম,
কারোর পেছনে হামাগুড়ি দিলুম,
তাদের পাঁজর কামড়ে ধরে ।
আকাশে, লা মারসেইলিজ-এর মতন লাল,
সূর্যাস্ত তার কম্পিত ঠোঁটে মরণশ্বাস তুলছিল ।
এটা মানসিক বিকার !
যুদ্ধ থেকে কোনো কিছুই বাঁচবে না ।
রাত এসে পড়বে,
কামড়ে ধরবে তোমাকে
আর বাসিই গিলে ফেলবে তোমাকে ।
দ্যাখো--
আকাশ আরেকবার জুডাস-এর ভূমিকায়,
একমুঠো নক্ষত্র নিয়ে কাদের বিশ্বাসঘাতকতায় চোবানো হয়েছিল?
এই রাত
তাতার যুদ্ধবাজ মামাই-এর মতন, আহ্লাদে পানোৎসব করে,
উত্তাপে দগ্ধ করে দিলো শহরকে ।
আমাদের চোখ এই রাতকে ভেদ করতে পারবে না,
দুই পক্ষের চর আজেফ-এর মতন কালো !
শুঁড়ির আসরে চুপচাপ এক কোণে হেলান দিয়ে, আমি বসে থাকি,
আমার আত্মায় আর মেঝেতে মদ চলকে পড়ে,
আর আমি দেখি :
কোনের দিকে, গোল চোখের প্রভা
আর তাদের সঙ্গে, ম্যাডোনা চেবাচ্ছে হৃদয়ের কেন্দ্র ।
এরকম মাতাল ভিড়ে অমন আনন্দবিচ্ছুরণ প্রদান করা কেন ?
ওদের কিই বা দেবার আছে ?
তোমরা দেখতে পাচ্ছ -- আরেকবার,
ওরা কেন বারাব্বাসকে পছন্দ করে
গোলগোথার মানুষটির তুলনায় ?
হয়তো, ভেবেচিন্তে,
মানবিক ভানে, কেবল একবার নয়
আমি কি তরতাজা মুখ পরে থাকবো ।
আমি, হয়তো,
তোমার ছেলেদের মধ্যে সবচেয়ে সৌম্যকান্তি
সম্পূর্ণ মানবজাতিতে ।
ওদের দিয়ে দাও,
যারা আহ্লাদে ডগমগ,
এক দ্রুত মৃত্যু,
যাতে ওদের ছেলেপুলেরা ভালোভাবে গড়ে ওঠে ;
ছেলেরা -- পিতা হিসাবে
মেয়েরা -- গর্ভবতী নারী হিসাবে ।
সেই জ্ঞানী মানুষদের মতন, নব্যপ্রসূতদের
অন্তর্দৃষ্টি আর ভাবনাচিন্তায় ধূসর হয়ে উঠতে দাও
আর ওরা আসবে
শিশুদের নামকরণের অনুষ্ঠানে
যে কবিতাগুলো আমি লিখেছি, তাদের।
আমি যন্ত্রপাতি আর ব্রিটেনের শিল্পের গুণগান করি ।
কোনো মামুলি, সার্বজনিক ধর্মোপদেশে,
হয়তো লেখা হয়ে থাকতে পারে
যে আমিই ত্রয়োদশতম দূত ।
আর যখন আমার কন্ঠস্বর তারস্বরে ঘোষণা করবে,
প্রতি সন্ধ্যায়,
ঘণ্টার পর ঘণ্টা,
আমার আহ্বানের অপেক্ষায়
যিশুখ্রিস্ট, নিজে, হয়তো ঘ্রাণ নেবেন
আমার আত্মার ফরগেট-মি-নট গুল্মের ।
চতুর্থ পর্ব
মারিয়া ! মারিয়া !
ভেতরে আসতে দাও, মারিয়া !
আমাকে রাস্তায় ফেলে যেও না !
তুমি অমন করতে পারো ?
আমার গাল চুপসে গেছে,
অথচ তুমি নিষ্ঠুরভাবে অপেক্ষা করাও ।
তাড়াতাড়ি, সবায়ের দ্বারা পরীক্ষিত,
বাসি আর বিবর্ণ,
আমি চলে আসবো
আর বিনা দাঁতে তোতলাবো
যে আজকে আমি
“সাতিশয় অকপট।”
মারিয়া,
চেয়ে দ্যাখো--
আমার কাঁধ দুটো আবার ঝুলে পড়ছে ।
রাস্তায়, লোকেরা
তাদের চার-তলা পেটের চর্বিতে আঙুল বোলায়।
ওরা চোখ দেখায়,
চল্লিশ বছরের অবসাদে ক্ষয়িত, আর অস্হির---
ওরা চাপা হাসি হাসে কেননা
আমার দাঁতে,
আবারও,
আমি গত রাতের আদরগুলোর শক্ত-হয়ে-যাওয়া ধৃষ্টতা কামড়ে ধরে রেখেছি ।
বৃষ্টি ফুটপাথের ওপরে কেঁদে ফেললো,--
ও তো জমা-জলে কারারুদ্ধ জোচ্চোর ।
রাস্তার লাশ, পাথরবাঁধানো পাথরের পিটুনি খেয়ে, নিজের কান্নায় ভিজে গেলো।
কিন্তু ধূসর চোখের পাতাগুলো--
হ্যাঁ !--
ঝুলন্ত বরফের চোখের পাতা হয়ে উঠলো জমাট
তাদের চোখ থেকে ঝরা অশ্রুজলে--
হ্যাঁ !--
ড্রেনপাইপগুলোর বিষাদভারাতুর চোখ থেকে ।
প্রতিটি পথচারীকে চাটছিল বৃষ্টির শুঁড় :
পথের গাড়িগুলোয় ঝিকমিক করছিল খেলোয়াড়ের দল ।
ফেটে পড়ছিল জনগণ
গাদাগাদি ভরা,
আর তাদের চর্বি উথলে উঠছিল ।
ঘোলাটে এক নদীর মতন, মাটিতে স্রোত গড়ে উঠেছিল,
তাতে মিশেছিল
বাসি মাংসের রস ।
মারিয়া !
কেমন করে আমি কোমল শব্দকে স্ফীত কানে আঁটাবো ?
একটা পাখি
ভিক্ষার জন্য গান গায়
ক্ষুধার্ত কন্ঠস্বরে
বরং ভালো,
কিন্তু আমি একজন মানুষ,
মারিয়া,
আমি তো প্রেসনিয়ার নোংরা তালুতে অসুস্হ রাতের কাশি ।
মারিয়া, তুমি কি আমাকে চাও ?
মারিয়া, আমাকে গ্রহণ করো, দয়া করো ।
কাঁপা আঙুলে আমি গির্জার ঘণ্টার লোহার গলা টিপে ধরবো !
মারিয়া !
রাস্তার চারণভূমিগুলো বুনো আর দর্শনীয় হয়ে গেছে !
ওরা আমার গলা টিপে ধরেছে আর আমি প্রায় অজ্ঞান হতে চলেছি।
খোলো !
আমি আহত !
দ্যাখো -- আমার চোখ খুবলে নেয়া হয়েছে
মেয়েদের টুপির আলপিন দিয়ে !
তুমি দরোজা খুলে দিলে ।
আমার খুকি !
ওহ, ভয় পেও না !
এই মহিলাদের দেখছো,
আমার গলায় পাহাড়ের মতন ঝুলে রয়েছে,--
জীবনভর, নিজের সঙ্গে টেনে নিয়ে যাই
কয়েক কোটি, প্রচুর, বিশাল, বিশুদ্ধ ভালোবাসাদের
আর কোটি কোটি নোংরা, বিদকুটে ভাড়াপ্রেমিকাদের ।
ভয় পেও না
যদি সততার
প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হয়,
হাজার সুন্দরী মুখ দেখে, আমি নিজেকে তাদের দিকে ছুঁড়ে দেবো--
“ওরা, যারা মায়াকভস্কিকে ভালোবাসে !”
দয়া করে বোঝো যে ওটাও হল
রানিদের বংশ, যারা একজন উন্মাদ মানুষের হৃদয়ে সওয়ার হয়েছে ।
মারিয়া, কাছে এসো !
নগ্ন আর লজ্জাহীন হও,
কিংবা আতঙ্কে শিহরিত,
তোমার ঠোঁটের বিস্ময়কে সমর্পণ করো, কতো নরম :
আমার হৃদয় আর আমি কখনও মে মাসের আগে পর্যন্ত থাকিনি,
কিন্তু অতীতে,
শত শত এপ্রিল মাস জড়ো হয়েছে ।
মারিয়া !
একজন কবি সারা দিন কল্পিত সুন্দরীর বন্দনায় গান গায়,
কিন্তু আমি--
আমি রক্তমাংসে গড়া,
আমি একজন মানুষ --
আমি তোমার দেহ চাই,
খ্রিস্টধর্মীরা যেমন প্রার্থনা করে :
“এই দিনটা আমাকে দাও
আমাদের প্রতিদিনের রুটি।”
মারিয়া, আমাকে দাও !
মারিয়া !
আমি ভয় পাই তোমার নাম ভুলে যাবো
চাপে পড়ে কবি যেমন শব্দ ভুলে যায়
একটি শব্দ
সে অস্হির রাতে কল্পনা করেছিল,
ঈশ্বরের সমান যার প্রভাব ।
তোমার দেহকে
আমি ভালোবেসে যাবো আর তত্বাবধান করবো
যেমন একজন সৈনিক
যুদ্ধে যার পা কাটা গেছে,
একা
আর-কেউ তাকে চায় না,
অন্য পা-কে সে সস্নেহে যত্ন করে ।
মারিয়া,--
তুমি কি আমাকে নেবে না ?
নেবে না তুমি !
হাঃ !
তাহলে অন্ধকারময় আর বেদনাদায়ক,
আরেকবার,
আমি বয়ে নিয়ে যাবো
আমার অশ্রু-কলঙ্কিত হৃদয়
এগোবো,
কুকুরের মতন,
খোঁড়াতে খোঁড়াতে,
থাবা বইতে থাকে সে
যার ওপর দিয়ে দ্রুতগতি রেলগাড়ি চলে গেছে।
হৃদয় থেকে রক্ত ঝরিয়ে আমি যে রাস্তায় ঘুরে বেড়াই তাকে উৎসাহ দেবো,
আমার জ্যাকেটে ফুলের গুচ্ছ ঝুলে থাকে, ধূসরিত করে,
সূর্য পৃথিবীর চারিধারে হাজার বার নাচবে,
স্যালোম-এর মতন
ব্যাপটিস্টের মুণ্ডু ঘিরে যে নেচে ছিল ।
আর যখন আমার বছরগুলো, একেবারে শেষে,
তাদের নাচ শেষ করবে আর বলিরেখা আঁকবে
কোটি কোটি রক্ত-কলঙ্ক ছড়িয়ে পড়বে
আমার পিতার রাজত্বের পথ
আমি চড়ে বেরিয়ে আসবো
নোংরা ( রাতের বেলায় গলিতে ঘুমিয়ে ),
আর কানেতে ফিসফিস করে বলব
যখন আমি দাঁড়িয়ে
ওনার দিকে :
শ্রীমান ঈশ্বর, শোনো !
এটা কি ক্লান্তিকর নয়
তোমার মহানুভব চোখদুটো মেঘেতে ডুবিয়ে দাও
প্রতিদিন, প্রতি সন্ধ্যায় ?
তার বদলে, এসো,
বৃত্তাকারে পাক খাবার উৎসব আরম্ভ করা যাক
শুভ আর অশুভের জ্ঞানবৃক্ষ ঘিরে !
সর্বশক্তিমান, তুমি চিরকাল আমাদের পাশে থাকবে !
মদ থেকে, মজাগুলো আরম্ভ হবে
আর প্রেরিত দূত পিটার, যিনি সব সময়ে ভ্রুকুটি করেন,
দ্রুত-লয়ের নাচ নাচবেন--- কি-কা-পু ।
আমরা সব কয়জন ইভকে ইডেন স্বর্গোদ্যানে ফিরিয়ে আনবো :
আমাকে আদেশ করো
আর আমি যাবো --
বীথিকাগুলো থেকে, প্রয়োজনের সুন্দরী মেয়েদের বেছে নেবো
আর তাদের তোমার কাছে আনবো !
আনবো তো আমি ?
না ?
তুমি তোমার কোঁকড়াচুল মাথা কেন অভব্যভাবে নাড়াচ্ছো ?
কেন তুমি তোমার ভ্রুতে গিঁট ফেলছো যেন তুমি রুক্ষ ?
তুমি কি মনে করো
যে এই
যার ডানা আছে, সে কাছেই,
ভালোবাসার মানে জানে ?
আমিও একজন দেবদূত ; আগেও ছিলুম--
শর্করায় তৈরি মেশশাবকের চোখ নিয়ে, আমি তোমার মুখগুলোর দিকে তাকালুম,
কিন্তু আমি ঘোটকিদের আর উপহার দিতে চাই না, --
সেভরে-পাড়ার সমস্ত অত্যাচারকে ফুলদানির রূপ দেয়া হয়েছে ।
সর্বশক্তিমান, তুমি দুটো হাত তৈরি করে দিয়েছো,
আর তা সযত্নে,
একটা মাথা গড়ে দিয়েছো, আর তালিকায় অনেককিছু রয়েছে--
কিন্তু কেন তুমি তা করলে
কেননা ব্যথা করে
যখন কেউ চুমু খায়, চুমু, চুমু ?!
আমি ভেবেছিলুম তুমিই মহান ঈশ্বর, সর্বশক্তিমান
কিন্তু তুমি একজন ক্ষুদে মূর্তি, -- স্যুট-পরা একজন নির্বোধ,
ঝুঁকে, আমি ইতিমধ্যে আয়ত্বে পেয়েছি
সেই ছুরি যা আমি লুকিয়ে রেখেছি
আমার বুটজুতোর ফাঁকে ।
তোমরা, ডানাসুদ্ধ জোচ্চোরের দল
ভয়ে জড়োসড়ো হও !
নিজেদের কাঁপতে-থাকা পালকগুলো ঝাঁকাও, রাসকেলের দল !
তুমি, গা থেকে ধুপের গন্ধ বেরোচ্ছে, তোমাকে চিরে ফালাফালা করব,
এখান থেকে আলাস্কা পর্যন্ত ধাওয়া করে।
আমাকে যেতে দাও !
তুমি আমাকে থামাতে পারবে না !
আমি ঠিক হই বা ভুল
তাতে কোনো তফাত হয় না,
আমি শান্ত হবো না ।
দ্যাখো,--
সারা রাত নক্ষত্রদের মাথা কাটা হয়েছে
আর আকাশ আবার কোতলে রক্তবর্ণ ।
ওহে তুমি,
স্বর্গ !
মাথা থেকে টুপি খোলো,
যখনই আমাকে কাছে দেখতে পাবে !
স্তব্ধতা ।
ব্রহ্মাণ্ড ঘুমোচ্ছে ।
কালো, নক্ষত্রে- কানের তলায়
থাবা রেখে ।
মেরুদণ্ড বেণু
প্রস্তাবনা
তোমাদের সকলের জন্যে,
যারা কখনও আনন্দ দিয়েছিল বা এখনও দিচ্ছে,
আত্মার সমাধিতে প্রতিমাদের দ্বারা সুরক্ষিত,
আমি তুলে ধরব, মদের এক পানপাত্রের মতো
উৎসবের অনুষ্ঠানে, খুলির কানায়-কানায় ভরা কবিতা ।
.
আমি প্রায়ই বেশি-বেশি ভাবি :
আমার জন্যে অনেক ভালো হতে পারতো
একটা বুলেট দিয়ে আমার সমাপ্তিকে বিদ্ধ করে দেয়া ।
আজকের দিনেই,
হয়তো বা,
আমি আমার অন্তিম প্রদর্শন মঞ্চস্হ করছি।
.
স্মৃতি !
আমার মগজ থেকে সভাঘরে একত্রিত হয়
আমার প্রেমের অফুরান সংখ্যা
চোখ থেকে চোখে হাসি ছড়িয়ে দ্যায় ।
বিগত বিয়ের ফেস্টুনে রাতকে সাজাও।
দেহ থেকে দেহে ঢেলে দাও আনন্দ ।
এই রাত যেন কেউ ভুলতে না পারে ।
এই অনুষ্ঠানে আমি বেণু বাজাব ।
বাজাবো আমার নিজের মেরুদণ্ডে ।
.
১
বড়োবড়ো পা ফেলে আমি মাড়িয়ে যাচ্ছি দীর্ঘ পথ ।
কোথায় যাবো আমি, নিজের ভেতরের নরকে লুকোবো ?
অভিশপ্ত নারী, কোন স্বর্গীয় কার্যাধ্যক্ষ
তার কল্পনায় তোমাকে গড়েছে ?!
আনন্দে মাতার জন্য পথগুলো অনেক বেশি সঙ্কীর্ণ ।
ছুটির দিনের গর্ব আর শোভাযাত্রায় জনগণ বেরিয়ে পড়েছে রবিবারের সাজে।
আমি ভাবলুম,
ভাবনাচিন্তা, অসুস্হ আর চাপচাপ
জমাটবাঁধা রক্ত, আমার খুলি থেকে হামাগুড়ি দিয়েছে ।
.
আমি,
যাকিছু উৎসবময় তার ইন্দ্রজালকর্মী,
এই উৎসব বাঁটোয়ারা করার কোনো সঙ্গী নেই।
এবার আমি যাবো আর ঝাঁপাবো,
নেভস্কির পাথরগুলোতে ঠুকবো আমার মগজ !
আমি ঈশ্বরনিন্দা করেছি ।
চিৎকার করে বলেছি ঈশ্বর বলে কিছু নেই,
কিন্তু নরকের অতল থেকে
ঈশ্বর এক নারীকে অবচিত করলেন যার সামনে পর্বতমালা
কাঁপবে আর শিহরিত হবে :
তিনি তাকে সামনে নিয়ে এলেন আর হুকুম দিলেন :
একে ভালোবাসো !
.
ঈশ্বর পরিতৃপ্ত ।
আকাশের তলায় এক দুরারোহ পাআড়ে
এক যন্ত্রণাকাতর মানুষ পশুতে পরিণত হয়ে বিদ্ধস্ত হয়েছে ।
ঈশ্বর হাত কচলান ।
ঈশ্বর চিন্তা করেন :
তুমি অপেক্ষা করো, ভ্লাদিমির !
যাতে তুমি জানতে না পারো নারীটি কে,
তিনি ছিলেন, নিঃসন্দেহে তিনি,
যিনি নারীটিকে একজন বাস্তব স্বামী দেবার কথা ভাবলেন
আর পিয়ানোর ওপরে মানুষের স্বরলিপি রাখলেন ।
কেউ যদি হঠাৎ পা-টিপে-টিপে শোবার ঘরের দরোজায় যেতো
আর তোমার ওপরের ওয়াড়-পরানো লেপকে আশীর্বাদ করতো,
আমি জানি
পোড়া পশমের গন্ধ বেরোতো,
আর শয়তানের মাংস উদ্গীরণ করতো গন্ধকের ধোঁয়া।
তার বদলে, সকাল হওয়া পর্যন্ত,
আতঙ্কে যে ভালোবাসবার জন্য তোমাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে
আমি ছোটাছুটি করলুম
আমার কান্নাকে কবিতার মুখাবয়ব দিলুম,
উন্মাদনার কিনারায় এক হীরক-কর্তনকারী।
ওহ, কেবল এক থাক তাসের জন্য !
ওহ, মদের জন্য
শ্বাসে বেরোনো হৃদয়কে কুলকুচি করার জন্য ।
.
তোমাকে আমার প্রয়োজন নেই !
তোমাকে আমি চাই না !
যাই হোক না কেন,
আমি জানি
আমি তাড়াতাড়ি কর্কশ চিৎকারে ভেঙে পড়ব !
.
যদি সত্যি হয় যে তোমার অস্তিত্ব আছে,
ঈশ্বর,
আমার ঈশ্বর,
যদি নক্ষত্রদের জাজিম তোমারই বোনা হয়,
যদি, প্রতিদিনকার এই
অতিরক্ত যন্ত্রণা,
তুমি চাপিয়ে দিয়েছ নিগ্রহ, হে প্রভু ;
তাহলে বিচারকের শেকল পরে নাও ।
আমার আগমনের জন্য অপেক্ষা করো।
আমি সময়কে মান্যতা দিই
এবং এক দিনও দেরি করব না ।
শোনো,
সর্বশক্তিমান ধর্মবিচারক !
আমি মুখে কুলুপ দিয়ে রাখব ।
কোনো কান্না
আমার কামড়ে-ধরা ঠোঁট থেকে বেরোবে না।
ঘোড়ার ল্যাজের মতো ধুমকেতুর সঙ্গে আমাকে বেঁধে রাখো,
আর ঘষটে নিয়ে চলো আমাকে,
নক্ষত্রদের গ্রাসে ছিন্ন হয়ে ।
কিংবা হয়তো এরকম :
আমার আত্মা যখন দেহের আশ্রয় ছেড়ে
তোমার বিচারব্যবস্হার সামনে নিজেকে উপস্হিত করবে,
তখন কটমট ভ্রু কুঁচকে,
তুমি,
ছায়াপথের দুই পাশে পা ঝুলিয়ে ছুঁড়ে দিও ফাঁসির দড়ি,
একজন অপরাধীর মতন আমাকে গ্রেপ্তার করে ঝুলিয়ে দিও ।
তোমার ইচ্ছানুযায়ী যা হয় কোরো।
যদি চাও আমাকে কেটে চার টুকরো করো।
আমি নিজে তোমার হাত ধুয়ে পরিষ্কার করে দেবো ।
কিন্তু এইটুকু করো--
তুমি কি শুনতে পাচ্ছো !---
ওই অভিশপ্ত নারীকে সরিয়ে দাও
যাকে তুমি আমার প্রিয়তমা করেছো !
.
বড়ো বড়ো পা ফেলে আমি মাড়িয়ে যাচ্ছি দীর্ঘ পথ ।
কোথায় যাবো আমি, নিজের ভেতরের নরকে লুকোবো ?
অভিশপ্ত নারী, কোন স্বর্গীয় কার্যাধ্যক্ষ
তার কল্পনায় তোমাকে গড়েছে ?!
.
২
উভয় আলোয়,
ধোঁয়ায় ভুলে গিয়েছে তার রঙ ছিল নীল,
আর মেঘগুলো দেখতে ছেঁড়াখোড়া উদ্বাস্তুদের মতো,
আমি নিয়ে আসবো আমার শেষতম ভালোবাসার ভোর,
কোনো ক্ষয়রোগীর রক্তবমির মতন উজ্বল।
উল্লাসময়তায় আমি ঢেকে ফেলবো গর্জন
সমাগমকারীদের,
বাড়ি আর আরাম সম্পর্কে বিস্মৃত।
পুরুষের দল,
আমার কথা শোনো !
পরিখা থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরোও :
তোমরা এই যুদ্ধ আরেকদিন লোড়ো।
.
এমনকি যদি,
মদ্যপানের গ্রিক দেবতার মতন রক্তে লুটোপুটি খাও,
এক মত্ত লড়াই তার শীর্ষে পৌঁছে গেছে--
তবুও ভালোবাসার শব্দেরা পুরোনো হয় না ।
প্রিয় জার্মানরা !
আমি জানি
গ্যেটের গ্রেশেন নামের নারী
তোমার ঠোঁটে উৎসারিত হয় ।
ফরাসিরা
বেয়োনেটের আঘাতে হাসিমুখে মারা যায় ;
মৃদু হাসি নিয়ে বিমানচালক ভেঙে পড়ে ;
যখন তাদের মনে পড়ে
তোমার চুমুখাওয়া মুখ,
ত্রাভিয়াতা ।
.
কিন্তু গোলাপি হাঁ-মুখের জন্য আমার আগ্রহ নেই
যা বহু শতক এতাবৎ কামড়েছে ।
আজকে আমাকে জড়িয়ে ধরতে দাও নতুন পা!
তুমি আমি গাইবো,
লালমাথায়
রুজমাখা ঠোঁটে ।
হয়তো, এই সময়কে কাটিয়ে উঠে
যা বেয়োনেটের ইস্পাতের মতন যন্ত্রণাদায়ক,
পেকে-যাওয়া দাড়িতে বহু শতক
কেবল আমরাই থাকবো :
তুমি
আর আমি,
শহর থেকে শহরে তোমার পেছন পেছন ।
সমুদ্রের ওই পারে তোমার বিয়ে হবে,
আর রাতের আশ্রয়ে প্রতীক্ষা করবে---
লণ্ডনের কুয়াশায় আমি দেগে দেবো
তোমায় পথলন্ঠনের তপ্ত ঠোঁট ।
এক গুমোটভরা মরুভূমিতে, যেখানে সিংহেরা সতর্ক,
তুমি তোমার কাফেলাদের মেলে ধরবে--
তোমার ওপরে,
হাওয়ায় ছেঁড়া বালিয়াড়ির তলায়,
আমি পেতে দেবে সাহারার মতন আমার জ্বলন্ত গাল।
.
তোমার ঠোঁটে এক চিলতে হাসি খেলিয়ে
তুমি চাউনি মেলবে
আর দেখবে এক সৌম্যকান্তি বুলফাইটার !
আর হঠাৎ আমি,
এক মরণাপন্ন ষাঁড়ের চোখের জন্য,
ধনী দর্শকদের দিকে আমার ঈর্ষা ছুঁড়ে দেবো ।
.
যদি কোনো সেতু পর্যন্ত তুমি তোমার সংশয়াপন্ন পা নিয়ে যাও,
এই ভেবে
নিচে নামা কতো ভালো--
তাহলে সে আমিই,
সেতুর তলা দিয়ে বয়ে যাচ্ছে সিন নদী,
যে তোমাকে ডাকবে
আমার ক্ষয়াটে দাঁত দেখিয়ে ।
.
যদি তুমি, অন্য পুরুষের সাথে মোটর গাড়িতে দ্রুত চলে যাচ্ছো, পুড়িয়ে দাও
স্ত্রেলকা-পাড়া বা সোকোলনিকি অঞ্চল--
তাহলে সে আমিই, উঁচুতে উঠছি,
চাঁদের মতন প্রত্যাশী আর আবরণমুক্ত,
যে তোমাকে আকাঙ্খায় আকুল করে তুলবে ।
.
তাদের প্রয়োজন হবে
আমার মতো এক শক্তিমান পুরুষ--
তারা হুকুম করবে :
যুদ্ধে গিয়ে মরো !
শেষ যে শব্দ আমি বলব
তা তোমার নাম,
বোমার টুকরোয় জখম আমার রক্তজমাট ঠোঁটে ।
.
আমার শেষ কি সিংহাসনে বসে হবে ?
নাকি সেইন্ট হেলেনা দ্বীপে ?
জীবনের ঝড়ের দাপটগুলোকে জিন পরিয়ে,
আমি প্রতিযোগীতায় নেমেছি
জগতের রাজত্বের জন্য
আর
দণ্ডাদেশ-পাওয়া কয়েদির পায়ের বেড়ি ।
.
আমি জার হবার জন্য নিয়তি-নির্দিষ্ট--
আমার মুদ্রার সূর্যালোকপ্রাপ্ত সোনায়
আমি আমার প্রজাদের হুকুম দেবো
টাঁকশালে ছাপ দিতে
তোমার চমৎকার মুখাবয়ব !
কিন্তু যেখানে
পৃথিবী হিমপ্রান্তরে বিলীন হয়,
নদী যেখানে উত্তর-বাতাসের সঙ্গে দরাদরি করে,
সেখানে আমি পায়ের বেড়িতে লিলির নাম আঁচড়ে লিখে যাবো,
আর কঠোর দণ্ডাদেশের অন্ধকারে,
বারবার তাতে চুমু খাবো ।
.
তোমরা শোনো, যারা ভুলে গেছ আকাশের রঙ নীল,
যারা সেই রকম রোমশ হয়েছ
যেন জানোয়ার ।
হয়তো এটাই
জগতের শেষতম ভালোবাসা
যা ক্ষয়রোগীর রক্তবমির মতন উজ্বল ।
.
৩
আমি ভুলে যাব বছর, দিন, তারিখ ।
কাগজের এক তাড়া দিয়ে নিজেকে তালাবন্ধ করে রাখব।
আলোকপ্রাপ্ত শব্দাবলীর যন্ত্রণার ভেতর দিয়ে,
সৃষ্টি করব তোমায়, হে অমানবিক ইন্দ্রজাল !
.
এই দিন, তোমার কাছে গিয়ে,
আমি অনুভব করেছি
বাড়িতে কিছু-একটা অঘটন ঘটেছে ।
তোমার রেশমে কিছু গোপন করেছ,
আর ধূপের সুগন্ধ ফলাও হয়ে ছড়িয়েছে বাতাসে ।
আমাকে দেখে আনন্দিত তো ?
সেই “অনেক”
ছিল অত্যন্ত শীতল ।
বিভ্রান্তি ভেঙে ফেলল যুক্তির পাঁচিল ।
তপ্ত ও জ্বরে আক্রান্ত, আমি হতাশার স্তুপে আশ্রয় নিলুম ।
.
শোনো,
তুমি যা-ই করো না কেন,
তুমি শবকে লুকোতে পারবে না ।
সেই ভয়ানক শব্দ মাথার ওপরে লাভা ঢেলে দ্যায় ।
তুমি যা-ই করো না কেন,
তোমার প্রতিটি পেশীতন্তু
শিঙা বাজায়
যেন লাউডস্পিকার থেকে :
মেয়েটি মৃতা, মৃতা, মৃতা !
তা হতে পারে না,
আমাকে জবাব দাও ।
মিথ্যা কথা বোলো না !
( এখন আমি যাবো কেমন করে ? )
তোমার মুখাবয়বে তোমার দুই চোখ খুঁড়ে তোলে
দুটি গভীর কবরের ব্যাদিত অতল ।
.
কবরগুলো আরও গভীর হয় ।
তাদের কোনো তলদেশ নেই ।
মনে হয়
দিনগুলোর উঁচু মাচান থেকে আমি প্রথমে মাথা নামিয়ে লাফিয়ে পড়ব।
অতল গহ্বরের ওপরে আমি আমার আত্মাকে টেনে বাজিকরের দড়ি করে নিয়েছি
আর, শব্দদের ভোজবাজি দেখিয়ে, তার ওপরে টাল সামলাচ্ছি ।
.
আমি জানি
ভালোবাসা তাকে ইতিমধ্যে পরাস্ত করেছে ।
আমি অবসাদের বহু চিহ্ণ খুঁজে পাচ্ছি ।
আমার আত্মায় পাচ্ছি আমাদের যৌবন ।
হৃদয়কে আহ্বান জানাও দেহের উৎসবে ।
.
আমি জানি
আমাদের প্রত্যেককে এক নারীর জন্য চড়া দাম দিতে হবে ।
তুমি কি কিছু মনে করবে
যদি, ইতিমধ্যে,
তোমাকে তামাক-ধোঁয়ার পোশাকে মুড়ে দিই
প্যারিসের ফ্যাশনের বদলে ?
.
প্রিয়তমাষু,
প্রাচীনকালে যিশুর বার্তাবাহকদের মতন,
আমি হাজার হাজার পথ দিয়ে হাঁটবো ।
অনন্তকাল তোমার জন্য এক মুকুট তৈরি করেছে,
সেই মুকুটে আমার শব্দাবলী
শিহরণের রামধনুর জাদু তৈরি করে ।
.
হাতির দল যেমন শতমণ ওজনের খেলায়
পুরুর রাজার বিজয় সম্পূর্ণ করেছিল,
আমি তোমার মগজে ভরে দিয়েছি প্রতিভার পদধ্বনি ।
কিন্তু সবই বৃথা ।
আমি তোমাকে বিচ্ছিন্ন করে আনতে পারি না ।
.
আনন্দ করো !
আনন্দ করো,
এখন
তুমি আমাকে শেষ করে দিয়েছ !
আমার মানসিক যন্ত্রণা এতোটাই তীক্ষ্ণ,
আমি ছুটে চলে যাবো খালের দিকে
আর মাথা চুবিয়ে দেবো তার অপূরণীয় গর্তে ।
.
তুমি তোমার ঠোঁট দিয়েছিলে ।
তুমি ওদের সঙ্গে বেশ রুক্ষ ছিলে ।
আমি হিম হয়ে গেলুম ছুঁয়ে ।
অনুতপ্ত ঠোঁটে আমি বরং চুমু খেতে পারতুম
জমাট পাথর ভেঙে তৈরি সন্ন্যাসিনীদের মঠকে ।
.
দরোজায়
ধাক্কা ।
পুরুষটি প্রবেশ করলো,
রাস্তার হইচইয়ে আচ্ছাদিত ।
আমি
টুকরো হয়ে গেলুম হাহাকারে ।
কেঁদে পুরুষটিকে বললুম :
“ঠিক আছে,
আমি চলে যাবো,
ঠিক আছে !
মেয়েটি তোমার কাছেই থাকবে ।
মেয়েটিকে সুচারু ছেঁড়া পোশাকে সাজিয়ে তোলো,
আর লাজুক ডানা দুটো, রেশমে মোড়া, মোটা হয়ে উঠুক।
নজর রাখো যাতে না মেয়েটি ভেসে চলে যায় ।
তোমার স্ত্রীর গলা ঘিরে
পাথরের মতন, ঝুলিয়ে দাও মুক্তোর হার ।”
.
ওহ, কেমনতর
এক রাত !
আমি নিজেই হতাশার ফাঁস শক্ত করে বেঁধে নিয়েছি ।
আমার ফোঁপানি আর হাসি
আতঙ্কে শোচনীয় করে তুলেছে ঘরের মুখ ।
তোমার দৃষ্টিপ্রতিভার বিধুর মুখাকৃতি জেগে উঠলো ;
তোমার চোখদুটি জাজিমের ওপরে দীপ্ত
যেন কোনো নতুন জাদুগর ভেলকি দেখিয়ে উপস্হিত করেছে
ইহুদি স্বর্গরাজ্যের ঝলমলে রানিকে ।
.
নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণায়
মেয়েটির সামনে যাকে আমি সমর্পণ করে দিয়েছি
আমি হাঁটু গেড়ে বসি ।
রাজা অ্যালবার্ট
তাঁর শহরগুলোকে
সমর্পণের পর
আমার তুলনায় ছিলেন উপহারে মোড়া জন্মদিনের খোকা ।
.
ফুলেরা আর ঘাসভূমি, সূর্যালোকে সোনার হয়ে গেল !
বাসন্তী হয়ে ওঠো, সমস্ত প্রাকৃতিক শক্তির জীবন !
আমি চাই একটিমাত্র বিষ--
কবিতার একটানা গভীর চুমুক ।
.
আমার হৃদয়ের চোর,
যে তার সমস্তকিছু ছিনতাই করেছে,
যে আমার আত্মাকে পীড়ন করে চিত্তবিভ্রম ঘটিয়েছে,
গ্রহণ করো, প্রিয়তমা, এই উপহার--
আর কখনও, হয়তো, আমি অন্যকিছু সম্পর্কে ভাববো না ।
.
এই দিনটিকে উজ্বল ছুটির দিনে রাঙিয়ে দাও ।
হে ক্রুশবিদ্ধসম ইন্দ্রজাল,
তোমার সৃষ্টি বজায় রাখো ।
যেমনটা দেখছো--
শব্দাবলীর পেরেকগুচ্ছ
আমাকে কাগজে গিঁথে দাও ।
.
শোনো !
শোনো
যদি নক্ষত্রদের আলোকিত করা হয়
তার মানে -- কেউ একজন আছে যার তা দরকার।
তার মানে -- কেই একজন চায় তা হোক,
কেউ একজন মনে করে থুতুর ওই দলাগুলো
অসাধারণ ।
আর অতিমাত্রায় উত্তেজিত,
দুপুরের ধুলোর ঘুর্নিপাকে,
ও ঈশ্বরের ওপর ফেটে পড়ে,
ভয়ে যে হয়তো সে ইতোমধ্যে দেরি করে ফেলেছে ।
চোখের জলে,
ও ঈশ্বরের শিরাওঠা হাতে চুমু খায়
কোথাও তো নিশ্চয়ই একটা নক্ষত্র থাকবে, তাই ।
ও শপথ করে
ও সহ্য করতে পারবে না
ওই নক্ষত্রহীন অদৃষ্ট ।
পরে,
ও ঘুরে বেড়ায়, উদ্বেগে,
কিন্তু বাইরে থেকে শান্ত ।
আর অন্য সবাইকে, ও বলে :
‘এখন,
সবকিছু ঠিক আছে
তুমি আর ভীত নও
সত্যি তো ?’
শোনো,
যদি নক্ষত্ররা আলোকিত হয়,
তার মানে - কেউ একজন আছে যার তা দরকার।
তার মানে এটা খুবই জরুরি যাতে
প্রতিটি সন্ধ্যায়
অন্তত একটা নক্ষত্র ওপরে উঠে যাবে
অট্টালিকার শীর্ষে ।
লিলিচকা
তামাকের ধোঁয়া বাতাসকে গ্রাস করেছে ।
ঘরটা
ক্রুচেনিখের নরকের একটা পর্ব ।
মনে রেখো --
ওই জানালার ওদিকে
রয়েছে প্রবল উত্তেজনা
আমি প্রথমে তোমার হাতে টোকা দিয়েছিলুম ।
আজ তুমি এখানে বসে আছো
লৌহবর্ম হৃদয়ে ।
আরেক দিন পরে
তুমি আমাকে তাড়িয়ে দেবে,
হয়তো, গালমন্দ করে ।
সামনের প্রায়ান্ধকার ঘরে আমার বাহু,
কাঁপুনিতে ভেঙে গেছে আর শার্টের হাতায় ঢুকবে না ।
আমি বাইরে বেরিয়ে যাবে
রাস্তায় নিজের দেহ ছুঁড়ে ফেলব ।
আমি প্রলাপ বকব,
নিয়ন্ত্রণের বাইরে,
বিষাদে চুরমার ।
তা হতে দিও না
আমার প্রিয়া,
আমার প্রিয়তমা,
এখন দুজনে দুদিকে যাওয়া যাক।
তা সত্বেও
আমার প্রেম
অত্যন্ত ভারি
তোমার ওপরে
তুমি যেখানেই যাও না কেন।
আমাকে একবার শেষ চিৎকার করতে দাও
তিক্ততার, আঘাতে জর্জরিত হবার চিৎকার ।
তুমি যদি একটা ষাঁড়কে খাটিয়ে নিরতিশয় ক্লান্ত করে দাও
সে পালিয়ে যাবে,
শীতল জলে গিয়ে নেমে যাবে ।
তোমার ভালোবাসা ছাড়া
আমার
কোনো সমুদ্র নেই
আর তোমার প্রেম এমনকি চোখের জলে চাওয়া বিশ্রামটুকুও দেবে না ।
যখন এক ক্লান্ত হাতি শান্তি চায়
সে তপ্ত বালির ওপরও রাজকীয় কায়দায় শুয়ে পড়ে।
তোমার ভালোবাসা ছাড়া
আমার
কোনো সূর্য নেই,
কিন্তু আমি এমনকি জানি না তুমি কোথায় আর কার সঙ্গে রয়েছো।
এভাবে যদি তুমি কোনও কবিকে যন্ত্রণা দাও
সে
তার প্রেমিকাকে টাকা আর খ্যাতির জন্য বদনাম করবে,
কিন্তু আমার কাছে
কোনো শব্দই আনন্দময় নয়
তোমার ভালোবাসাময় নাম ছাড়া ।
আমি নিচের তলায় লাফিয়ে পড়ব না
কিংবা বিষপান করব না
বা মাথায় বন্দুক ঠেকাবো না ।
কোনো চাকুর ধার
আমাকে অসাড় করতে পারে না
তোমার চাউনি ছাড়া ।
কাল তুমি ভুলে যাবে যে
আমি তোমায় মুকুট পরিয়েছিলুম,
যে আমি আমার কুসুমিত আত্মাকে ভালোবাসায় পুড়িয়েছিলুম,
আর মামুলি দিনগুলোর ঘুরন্ত আনন্দমেলা
আমার বইয়ের পাতাগুলোকে এলোমেলো করে দেবে…
আমার শব্দগুলোর শুকনো পাতারা কি
শ্বাসের জন্য হাঁপানো থেকে
তোমাকে থামাতে পারবে ?
অন্তত আমাকে তোমার
বিদায়বেলার অপসৃত পথকে
সোহাগে ভরে দিতে দাও ।
তুমি
তুমি এলে--
কৃতসঙ্কল্প,
কেননা আমি ছিলুম দীর্ঘদেহী,
কেননা আমি গর্জন করছিলুম,
কিন্তু খুঁটিয়ে দেখে
তুমি দেখলে আমি নিছকই এক বালক ।
তুমি দখল করে নিলে
আর কেড়ে নিলে আমার হৃদয়
আর তা নিয়ে
খেলতে আরম্ভ করলে--
লাফানো বল নিয়ে মেয়েরা যেমন খেলে ।
আর এই অলৌকিক ঘটনার আগে
প্রতিটি নারী
হয়তো ছিল এক বিস্ময়বিহ্বল যুবতী
কিংবা এক কুমারী তরুণী যে জানতে চায় :
“অমন লোককে ভালোবাসবো ?
কেন, সে তোমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে !
মেয়েটি নিশ্চয়ই সিংহদের পোষ মানায়,
চিড়িয়াখানার এক মহিলা !”
কিন্তু আমি ছিলুম জয়োল্লাসিত ।
আমি ওটা অনুভব করিনি --
ওই জোয়াল !
আনন্দে সবকিছু ভুলে গিয়ে,
আমি লাফিয়ে উঠলুম
এদিকে-সেদিকে উৎক্রান্ত, কনে পাবার আনন্দে রেডিণ্ডিয়ান,
আমি খুবই গর্বিত বোধ করছিলুম
আর ফুরফুরে ।
 মলয় রায়চৌধুরী | 27.58.255.50 | ১০ আগস্ট ২০২১ ১৯:২৬734847
মলয় রায়চৌধুরী | 27.58.255.50 | ১০ আগস্ট ২০২১ ১৯:২৬734847হাংরি ও পরাবাস্তববাদের অবনিবনার অহেতুক চর্চা
মলয় রায়চৌধুরী
এক
হাংরি আন্দোলনকারীদের অবনিবনা নিয়ে যতো খিল্লি হয় তা কিন্তু পরাবাস্তববাদীদের মাঝে অবনিবনা নিয়ে হয় না । অথচ পরাবাস্তববাদীদের পরস্পরের ঝগড়া কতোজনের সঙ্গে যে প্রত্যেকের হয়েছিল তার কোনও হিসেব নেই । ফিদেল কাস্ত্রোর সঙ্গে চে গ্বেভারার অবনিবনা চেপে গিয়ে পালা করে ওই দুজনের টি শার্ট পরে ঘুরে বেড়ান বাঙালি ছোকরা লেখক-কবি। অথচ হাংরি আন্দোলনের আলোচনা শুরু করলেই সবাই তাঁদের পারস্পরিক অবনিবনা চর্চা করেন ; লেখালিখি বিশ্লেষণের কথা চিন্তা করেন না বা করতে চান না, বিশেষ করে বাঙালি আলোচকরা । নন্দিনী ধর হাংরি আন্দোলন আলোচনা করতে বসে দুম করে লিখে দিলেন যে আমার সংকলিত বই থেকে শৈলেশ্বর ঘোষকে বাদ দিয়েছি ; অথচ আমি হাংরি আন্দোলনকারীদের রচনার কোনো সংকলন প্রকাশ করিনি । নন্দিনী ধর লিখেছেন যে হাংরি আন্দোলনকারীরা নিজেদের ছোটোলোক ঘোষণা করে বিবিক্ততাকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন ; উনি জানতেন না যে আমি পাটনায় ইমলিতলা নামে এক অন্ত্যজ অধ্যুষিত বস্তিতে থাকতুম, অবনী ধর ছিলেন জাহাজের খালাসি আর পরে ঠেলাগাড়িতে করে কয়লা বেচতেন, শৈলেশ্বর ঘোষ আর সুভাষ ঘোষ এসেছিলেন উদ্বাস্তু পরিবার থেকে, দেবী রায় চায়ের ঠেকে চা বিলি করতেন । এ-থেকে টের পাওয়া যায় যে আলোচকরা কোনও বই পড়ার আগেই ভেবে নেন যে হাংরি আন্দোলনকারীদের রচনা আলোচনার সময়ে কী লিখবেন । হাংরি আন্দোলনকারীদের বিশ্ববীক্ষার তর্ক-বিতর্ক ও লেখালিখি বাদে দিয়ে আলোচকরা ব্যক্তিগত সম্পর্ককে গুরুত্ব দেন ।
অন্য বাঙালি লেখকদের ক্ষেত্রে কিন্তু তাঁরা এমন অডিটরসূলভ বিশ্লেষণ করতে বসেন না । বিদেশি সাহিত্যিকদের মাঝে নিজেদের বিশ্ববীক্ষার সমর্থনে পারস্পরিক বিবাদ-বিতর্কের কথা যেমন শোনা যায় তেমনটা বাঙালি লেখকদের ক্ষেত্রে বড়ো একটা দেখা যায় না । আমরা পড়েছি গোর ভিডাল আর নরম্যান মেইলারের বিবাদ এমনকি হাতাহাতি, সালমান রুশডি - জন আপডাইক বিবাদ, হেনরি জেমস - এইচ জি ওয়েল্স বিবাদ, জোসেফ কনরাড - ডি এইচ লরেন্স বিবাদ, জন কিটস - লর্ড বায়রন বিবাদ, চার্লস ডিকেন্স - হ্যান্স ক্রিশ্চিয়ান অ্যাণ্ডারসন বিবাদ ইত্যাদি । আলোচকরা কিন্তু তাঁদের রচনাবলী বিশ্লেষণের সময়ে সৃজনশীল কাজকেই গুরুত্ব দেন, বিবাদকে নয় ।
বাঙালি সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, মনে করেন মানুষ ও প্রাণীরা এসেছে অন্য গ্রহ থেকে, অনুকূল ঠাকুরের শিষ্য । ওই একই দপতরে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর পাশের কেবিনেই বসতেন ,যিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন না, ডারউইনের তত্বে বিশ্বাস করতেন, বামপন্হী ছিলেন । অথচ পরপস্পরের লেখা আলোচনার সময়ে এই বিষয়গুলো ওনাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যেত, যেন সাহিত্য আলোচনায় লেখকের বিশ্ববীক্ষার কোনো প্রভাব থাকে না । অধিকাংশ বাঙালি সাহিত্যিক এই ধরণের ভাই-ভাই ক্লাবের সদস্য । এদিকে হাংরি আন্দোলনকারীদের রচনা আলোচনা করতে বসে তাদের ব্যক্তিগত অবনিবনায় জোর দেন ।
এই তো সেদিন ক্লিন্টন বি সিলির জীবনানন্দ বিষয়ক গ্রন্হ ‘এ পোয়েট অ্যাপার্ট, পড়ার সময়ে হাংরি আন্দোলনকারীরা খালাসিটোলায় জীবনানন্দের যে জন্মদিন পালন করেছিল, তার বর্ণনা পড়ছিলুম । উনি ‘দি স্টেটসম্যান’ পত্রিকায় ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৮ তারিখে প্রকাশিত সংবাদ তুলে দিয়ে পরবর্তী প্রজন্মে জীবনানন্দের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেছেন । একই খবর প্রকাশিত হয়েছিল তখনকার সাপ্তাহিক ‘অমৃত’ পত্রিকায় । সেদিন সন্ধ্যায় জীবনানন্দ দাশের জন্মদিন পালনের জন্য টেবিলে উঠে পড়লেন হাংরি আন্দোলনের গল্পকার অবনী ধর আর নাচের সঙ্গে গাইতে লাগলেন একটা গান, যা তিনি জাহাজে খালসির কাজ করার সময়ে গাইতেন, বিদেশি খালাসিদের সঙ্গে । উপস্হিত সবাই, এমনকি হাংরি আন্দোলনের কয়েকজন ভেবেছিলেন গানটা আবোল-তাবোল, কেননা ইংরেজিতে তো এমনতর শব্দ তাঁদের জানা ছিল না । যে সাংবাদিকরা খবর কভার করতে এসেছিলেন তাঁরাও গানটাকে ভেবেছিলেন হাংরি আন্দোলনকারীদের বজ্জাতি, প্রচার পাবার ধান্দা । ‘অমৃত’ পত্রিকায় ‘লস্ট জেনারেশন’ শিরোনামে ঠাট্টা করে দুই পাতা চুটকি লেখা হয়েছিল, অবনী ধরের কার্টুনের সঙ্গে । ‘অমৃত’ পত্রিকায় ‘লস্ট জেনারেশন’ তকমাটি যিনি ব্যবহার করেছিলেন তিনি জানতেন না যে এই শব্দবন্ধ তৈরি করেছিলেন গারট্রুড স্টিন এবং বিশ শতকের বিশের দশকে প্যারিসে আশ্রয় নেয়া আর্নেস্ট হেমিংওয়ে, এফ স্কট ফিটজেরাল্ড, টি. এস. এলিয়ট, জন ডস প্যাসস, ই ই কামিংস, আর্চিবল্ড ম্যাকলিশ, হার্ট ক্রেন প্রমুখকে বলা হয়েছিল ‘লস্ট জেনারেশন’-এর সদস্য । অবনী ধর-এর নামের সঙ্গে অনেকেই পরিচিত নন । যাঁরা তাঁর নাম শোনেননি এবং ওনার একমাত্র বই ‘ওয়ান শট’ পড়েননি, তাঁদের জানাই যে ছোটোগল্পের সংজ্ঞাকে মান্যতা দিলে বলতে হয় যে অবনী ধর ছিলেন হাংরি আন্দোলনের সর্বশ্রেষ্ঠ ছোটো গল্পকার ।
গানটা এরকম, মোৎসার্টের একটা বিশেষ সুরে গাওয়া হয়:
জিং গ্যাং গুলি গুলি গুলি গুলি ওয়াচা,
জিং গ্যাং গু, জিং গ্যাং গু ।
জিং গ্যাং গুলি গুলি গুলি গুলি ওয়াচা,
জিং গ্যাং গু, জিং গ্যাং গু ।
হায়লা, ওহ হায়লা শায়লা, হায়লা শায়লা, শায়লা উউউউউহ,
হায়লা, ওহ হায়লা শায়লা, হায়লা শায়লা, শায়লা, উহ
শ্যালি ওয়ালি, শ্যালি ওয়ালি, শ্যালি ওয়ালি, শ্যালি ওয়ালি ।
উউউমপাহ, উউউমপাহ, উউউমপাহ, উউউমপাহ ।
১৯২০ সালে,, প্রথম বিশ্ব স্কাউট জাম্বোরির জন্য, রবার্ট ব্যাডেন-পাওয়েল, প্রথম বারন ব্যাডেন-পাওয়েল (স্কাউটিংয়ের প্রতিষ্ঠাতা) সিদ্ধান্ত নেন যে একটা মজার গান পেলে ভালো হয়, যা সব দেশের স্কাউটরা গাইতে পারবে ; কারোরই কঠিন মনে হবে না । উনি মোৎসার্টের এক নম্বর সিম্ফনির ইবি মেজরে বাঁধা সুরটি ধার করেছিলেন । গানটা স্কাউটদের মধ্যে তো বটেই সাধারণ স্কুল ছাত্রদের মধ্যেও জনপ্রিয় হয়েছিল । এই স্কাউটদের কেউ-কেউ জাহাজে চাকরি নিয়ে খালাসি এবং অন্যান্য কর্মীদের মধ্যে এটাকে ছড়িয়ে দিতে সফল হন । অবনী ধর বেশ কিছুকাল জাহাজে খালাসির কাজ করেছিলেন এবং তাঁরও ভালো লেগে যায় সমবেতভাবে গাওয়া গানটি । শতভিষা, কৃত্তিবাস, কবিতা, ধ্রুপদি পত্রিকার কর্নধারদের প্রিয় সঙ্গীত-জগত থেকে একশো আশি ডিগ্রি ঘুরে যাওয়া এই গান সেসময়ে নিতে পারেননি সাংবাদিক আর বিদ্যায়তনিক আলোচকরা, তার ওপর যেহেতু হাংরি আন্দোলনের ব্যাপার, তাই তাঁরা এটাকে অশিক্ষিত নেশাখোর-মাতালদের কারবার ভেবে হেঁ-হেঁ করে হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন ।
দুই
উত্তরবঙ্গে হাংরি জেনারেশনের প্রসার সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে, হাংরি পত্রিকা ‘কনসেনট্রেশন ক্যাম্প’ এর সম্পাদক অলোক গোস্বামী এই কথাগুলো লিখেছিলেন, তা থেকে অবনিবনার যৎসামান্য আইডিয়া হবে, আর এই অবনিবনার সঙ্গে পরাবাস্তববাদীদের নিজেদের অবনিবনারে যথেষ্ট মিল আছে :-
“নব্বুই দশকে সদ্য প্রকাশিত কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প বগলে নিয়ে এক ঠা ঠা দুপুরে আমি হাজির হয়েছিলাম শৈলেশ্বরের বাড়ির গেটে। একা। ইচ্ছে ছিল শৈলেশ্বরের সঙ্গে মুখোমুখি বসে যাবতীয় ভুল বোঝাবুঝি নিয়ে খোলাখুলি কথা বলবো। যেহেতু স্মরণে ছিল শৈলেশ্বরের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের স্মৃতি তাই আস্থা ছিল শৈলেশ্বরের প্রজ্ঞা,ব্যক্তিত্ব,যুক্তিবোধ তথা ভদ্রতাবোধের ওপর। দৃঢ় বিশ্বাস ছিল শৈলেশ্বর আমাদের ভুলগুলো ধরিয়ে দেবেন এবং যৌথ আলোচনাই পারবে সব ভুল বোঝাবুঝি মিটিয়ে নতুন উদ্যমে একসাথে পথ চলা শুরু করতে। কিন্তু দুভার্গ্য বশতঃ তেমন কিছু ঘটলো না। বেল বাজাতেই গেটের ওপারে শৈলেশ্বর। আমাকে দেখেই ভ্রূ কুঁচকে ফেললেন।
--কী চাই!
মিনমিন করে বললাম, আপনার সঙ্গে কথা বলবো।
--কে আপনি?
এক এবং দুই নম্বর প্রশ্নের ভুল অবস্থান দেখে হাসি পাওয়া সত্বেও চেপে গিয়ে নাম বললাম।
--কি কথা?
--গেটটা না খুললে কথা বলি কিভাবে!
--কোনো কথার প্রয়োজন নেই। চলে যান।
--এভাবে কথা বলছেন কেন?
--যা বলছি ঠিক বলছি। যান। নাহলে কিন্তু প্রতিবেশীদের ডাকতে বাধ্য হবো।
এরপর স্বাভাবিক কারণেই খানিকটা ভয় পেয়েছিলাম কারণ আমার চেহারাটা যেরকম তাতে শৈলেশ্বর যদি একবার ডাকাত, ডাকাত বলে চেঁচিয়ে ওঠেন তাহলে হয়ত জান নিয়ে ফেরার সুযোগ পাবো না। তবে 'ছেলেধরা' বলে চেল্লালে ভয় পেতাম না। সমকামিতার দোষ না থাকায় নির্ঘাত রুখে দাঁড়াতাম।
ভয় পাচ্ছি অথচ চলেও যেতে পারছি না। সিদ্ধান্তে পৌঁছতে গেলে আরও খানিকটা জানা বোঝা জরুরি।
--ঠিক আছে, চলে যাচ্ছি। তবে পত্রিকার নতুন সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে সেটা রাখুন।
এগিয়ে আসতে গিয়েও থমকে দাঁড়ালেন শৈলেশ্বর।
--কোন পত্রিকা?
--কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প।
--নেব না। যান।
এরপর আর দাঁড়াইনি। দাঁড়ানোর প্রয়োজনও ছিল না। ততক্ষণে বুঝে ফেলেছি ব্যক্তি শৈলেশ্বর ঘোষকে চিনতে ভুল হয়নি আমাদের। আর এই সমঝদারি এতটাই তৃপ্তি দিয়েছিল যে অপমানবোধ স্পর্শ করারই সুযোগ পায়নি।”
পরাবাস্তববাদীদের মতনই, শৈলেশ্বর ঘোষের হয়তো মনে হয়েছিল যে কলকাতায় তিনি হাংরি আন্দোলনের যে কেন্দ্র গড়ে তুলতে চাইছেন তাতে ফাটল ধরাবার চেষ্টা করা হচ্ছে । তাঁর আচরণ ছিল হুবহু আঁদ্রে ব্রেতঁর মতন । পরাবাস্তববাদ আন্দোলনে আঁদ্রে ব্রেতঁর সঙ্গে অনেকের সম্পর্ক ভালো ছিল না, দল বহুবার ভাগাভাগি হয়েছিল, অথচ সেসব নিয়ে বাঙালি আলোচকরা তেমন উৎসাহিত নন, যতোটা হাংরি আন্দোলনের দল-ভাগাভাগি নিয়ে। ইংরেজিতে মৈত্রেয়ী ভট্টাচার্য চৌধুরী হাংরি আন্দোলন নিয়ে ‘দি হাংরিয়ালিস্টস’ নামে একটি বই লিখেছেন, পেঙ্গুইন র্যাণ্ডাম হাউস থেকে প্রকাশিত । সেই বইটি বাংলা পত্রপত্রিকায় আলোচিত হল না ।
তিন
আনন্দবাজার পত্রিকায় ১৬ জুন ২০১৩ তারিখে গৌতম চক্রবর্তী হাংরি আন্দোলন সম্পর্কে এই কথাগুলো লিখেছিলেন ; তাতেও রয়েছে টিটকিরি, যা তিনি পরাবাস্তববাদীদের সম্পর্কে কখনও বলেছেন কিনা জানি না । উনি লিখেছিলেন :
“মানুষ, ঈশ্বর, গণতন্ত্র ও বিজ্ঞান পরাজিত হয়ে গেছে। কবিতা এখন একমাত্র আশ্রয়।... এখন কবিতা রচিত হয় অর্গ্যাজমের মতো স্বতঃস্ফূর্তিতে।
১৯৬২ সালে এই ভাষাতেই কলেজ স্ট্রিট কফি হাউস থেকে খালাসিটোলা, বারদুয়ারি অবধি সর্বত্র গোপন বিপ্লবী আন্দোলনের ব্লু প্রিন্টের মতো ছড়িয়ে পড়ে একটি ম্যানিফেস্টো। ২৬৯ নেতাজি সুভাষ রোড, হাওড়া থেকে প্রকাশিত এই ম্যানিফেস্টোর ওপরে লেখা ‘হাংরি জেনারেশন’। নীচের লাইনে তিনটি নাম। ‘স্রষ্টা: মলয় রায়চৌধুরী। নেতৃত্ব: শক্তি চট্টোপাধ্যায়। সম্পাদনা: দেবী রায়।’
তখনও কলেজ স্ট্রিটের বাতাসে আসেনি বারুদের গন্ধ, দেওয়ালে লেখা হয়নি ‘সত্তরের দশক মুক্তির দশক’। কিন্তু পঞ্চাশ পেরিয়ে-যাওয়া এই ম্যানিফেস্টোর গুরুত্ব অন্যত্র। এর আগে ‘ভারতী’, ‘কবিতা’, ‘কৃত্তিবাস’, ‘শতভিষা’ অনেক কবিতার কাগজ ছিল, সেগুলি ঘিরে কবিরা সংঘবদ্ধও হতেন। কিন্তু এই ভাবে সাইক্লোস্টাইল-করা ম্যানিফেস্টো আগে কখনও ছড়ায়নি বাংলা কবিতা।
ওটি হাংরি আন্দোলনের দ্বিতীয় ম্যানিফেস্টো। প্রথম ম্যানিফেস্টোটি বেরিয়েছিল তার কয়েক মাস আগে, ১৯৬১ সালের নভেম্বর মাসে। ইংরেজিতে লেখা সেই ম্যানিফেস্টো জানায়, কবিতা সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যায় না, বিভ্রমের বাগানে পুনরায় বৃক্ষরোপণ করে না। ‘Poetry is no more a civilizing manoeuvre, a replanting of bamboozled gardens.’ বিশ্বায়নের ঢের আগে ইংরেজি ভাষাতেই প্রথম ম্যানিফেস্টো লিখেছিলেন হাংরি কবিরা। কারণ, পটনার বাসিন্দা মলয় রায়চৌধুরী ম্যানিফেস্টোটি লিখেছিলেন। পটনায় বাংলা ছাপাখানা ছিল না, ফলে ইংরেজি।
দুটি ম্যানিফেস্টোতেই শেষ হল না ইতিহাস। হাংরি আসলে সেই আন্দোলন, যার কোনও কেন্দ্র নেই। ফলে শহরে, মফস্সলে যে কোনও কবিই বের করতে পারেন তাঁর বুলেটিন। ১৯৬৮ সালে শৈলেশ্বর ঘোষ তাঁর ‘মুক্ত কবিতার ইসতাহার’-এ ছাপিয়ে দিলেন ‘সমস্ত ভন্ডামির চেহারা মেলে ধরা’, ‘শিল্প নামক তথাকথিত ভূষিমালে বিশ্বাস না করা’, ‘প্রতিষ্ঠানকে ঘৃণা করা’, ‘সভ্যতার নোনা পলেস্তারা মুখ থেকে তুলে ফেলা’ ইত্যাদি ২৮টি প্রতিজ্ঞা। পরে বন্ধুদের মধ্যে ঝগড়া বাধবে। মলয় ব্যাংকের চাকরি নিয়ে বাইরে চলে যাবেন। শৈলেশ্বর, সুবো আচার্য এবং প্রদীপ চৌধুরীরা বলবেন, ‘মলয় বুর্জোয়া সুখ ও সিকিয়োরিটির লোভে আন্দোলন ছেড়ে চলে গিয়েছে।’কী রকম লিখতেন হাংরিরা? বছর দুয়েক আগে সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের ‘বাইশে শ্রাবণ’ ছবিতে গৌতম ঘোষের চরিত্রটি লেখা হয়েছিল হাংরি কবিদের আদলে।
‘জেগে ওঠে পুরুষাঙ্গ নেশার জন্য হাড় মাস রক্ত ঘিলু শুরু করে কান্নাকাটি
মনের বৃন্দাবনে পাড়াতুতো দিদি বোন বউদিদের সঙ্গে শুরু হয় পরকীয়া প্রেম’,
লিখেছিলেন অকালপ্রয়াত ফালগুনী রায়। র্যাঁবো, উইলিয়াম বারোজ এবং হেনরি মিলারের উদাহরণ বারে বারেই টেনেছেন হাংরিরা। ঘটনা, এঁরা যত না ভাল কবিতা লিখেছেন, তার চেয়েও বেশি ঝগড়া করেছেন। এবং তার চেয়েও বেশি বার গাঁজা, এলএসডি, মেস্কালিন আর অ্যাম্ফিটোমাইন ট্রিপে গিয়েছেন।
অতএব, সাররিয়ালিজ্ম বা অন্য শিল্প আন্দোলনের মতো বাঙালি কবিদের ম্যানিফেস্টোটি কোনও দিন গুরুত্বপূর্ণ হয়নি। কিন্তু ‘হাংরি’রা আজও মিথ। এক সময় ‘মুখোশ খুলে ফেলুন’ বলে তৎকালীন মন্ত্রী, আমলা, সম্পাদকদের বাড়িতে ডাকযোগে তাঁরা মুখোশ পাঠিয়ে দিয়েছেন। আবার এক সময় ‘প্রচন্ড বৈদ্যুতিক ছুতার’ কবিতাটি লেখার জন্য অশ্লীলতার মামলা হল মলয় রায়চৌধুরীর বিরুদ্ধে। উৎপলকুমার বসু, সুবিমল বসাকের বিরুদ্ধে জারি হল গ্রেফতারি পরোয়ানা।
রাষ্ট্র ও আদালত কী ভাবে কবিতাকে দেখে, সেই প্রতর্কে ঢুকতে হলে ১৯৬৫ সালে মলয় রায়চৌধুরীর বিরুদ্ধে মামলাটি সম্পর্কে জানা জরুরি। শক্তি চট্টোপাধ্যায় কাঠগড়ায় উঠেছেন মলয়ের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে। পাবলিক প্রসিকিউটরের জিজ্ঞাসা, ‘প্রচন্ড বৈদ্যুতিক ছুতার’ কবিতাটা পড়ে আপনার কী মনে হয়েছে?
শক্তি: ভাল লাগেনি।
প্রসিকিউটর: অবসিন কি? ভাল লাগেনি বলতে আপনি কী বোঝাতে চাইছেন?
শক্তি: ভাল লাগেনি মানে জাস্ট ভাল লাগেনি। কোনও কবিতা পড়তে ভাল লাগে, আবার কোনওটা ভাল লাগে না।
শক্তি সাক্ষ্য দিয়েছিলেন মলয়ের বিরুদ্ধে। কয়েক মাস পরে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় মলয়ের সমর্থনে...
প্রসিকিউটর: কবিতাটা কি অশ্লীল মনে হচ্ছে?
সুনীল: কই, না তো। আমার তো বেশ ভাল লাগছে। বেশ ভাল লিখেছে।
প্রসিকিউটর: আপনার শরীরে বা মনে খারাপ কিছু ঘটছে?
সুনীল: না, তা কেন হবে? কবিতা পড়লে সে সব কিছু হয় না।
একই মামলায় শক্তি ও সুনীল পরস্পরের বিরুদ্ধে। তার চেয়েও বড় কথা, ’৬৫ সালে এই সাক্ষ্য দেওয়ার আগের বছরই সুনীল আইওয়া থেকে মলয়কে বেশ কড়া একটি চিঠি দিয়েছিলেন, ‘লেখার বদলে আন্দোলন ও হাঙ্গামা করার দিকেই তোমার ঝোঁক বেশি। রাত্রে তোমার ঘুম হয় তো? মনে হয়, খুব একটা শর্টকাট খ্যাতি পাবার লোভ তোমার।’ ব্যক্তিগত চিঠিতে অনুজপ্রতিম মলয়কে ধমকাচ্ছেন, কিন্তু আদালতে তাঁর পাশে গিয়েই দাঁড়াচ্ছেন। সম্ভবত, বন্ধু-শত্রু নির্বিশেষে অনুজ কবিদের কাছে সুনীলের ‘সুনীলদা’ হয়ে ওঠা হাংরি মামলা থেকেই। প্রবাদপ্রতিম কৃত্তিবাসী বন্ধুত্বের নীচে যে কত চোরাবালি ছিল, তা বোঝা যায় উৎপলকুমার বসুকে লেখা সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের একটি চিঠি থেকে, ‘প্রিয় উৎপল, একদিন আসুন।...আপনি তো আর শক্তির মতো ধান্দায় ঘোরেন না।’
তা হলে কি হাংরি আন্দোলন বাংলা সাহিত্যে প্রভাবহীন, শুধুই কেচ্ছাদার জমজমাট এক পাদটীকা? দুটি কথা। হাংরিদের প্রভাবেই কবিতা-সংক্রান্ত লিট্ল ম্যাগগুলির ‘কৃত্তিবাস’, ‘শতভিষা’ গোছের নাম বদলে যায়। আসে ‘ক্ষুধার্ত’, ‘জেব্রা’, ‘ফুঃ’-এর মতো কাগজ। সেখানে কবিতায় বাঁকাচোরা ইটালিক্স, মোটাদাগের বোল্ড ইত্যাদি হরেক রকমের টাইপোগ্রাফি ব্যবহৃত হত। পরবর্তী কালে সুবিমল মিশ্রের মতো অনেকেই নিজেকে হাংরি বলবেন না, বলবেন ‘শুধুই ছোট কাগজের লেখক’। কিন্তু তাঁদের গল্প, উপন্যাসেও আসবে সেই টাইপোগ্রাফিক বিভিন্নতা। তৈরি হবে শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন। হাংরিরা না এলে কি নব্বইয়ের দশকেও হানা দিতেন পুরন্দর ভাট?
আসলে, ম্যানিফেস্টোর মধ্যেই ছিল মৃত্যুঘণ্টা। ’৬২ সালে হাংরিদের প্রথম বাংলা ম্যানিফেস্টোর শেষ লাইন, ‘কবিতা সতীর মতো চরিত্রহীনা, প্রিয়তমার মতো যোনিহীনা ও ঈশ্বরীর মতো অনুষ্মেষিণী।’ হাংরিরা নিজেদের যত না সাহিত্যবিপ্লবী মনে করেছেন, তার চেয়েও বেশি যৌনবিপ্লবী।”
চার
গৌতম চক্রবর্তী বহু বিদেশি নাম বাদ দিয়ে দিয়েছেন ; সম্ভবত তিনিও লেখার আগেই হাংরি আন্দোলনকারীদের ব্যঙ্গ করবেন বলে ঠিক করে ফেলেছিলেন । হাংরি আন্দোলনকারীরা জানতো যে ব্রিটিশ ঔপন্যাসিক চার্লস ডিকেন্স তিনি মর্গে যেতে ভালোবাসতেন; সেখানে দিনের একটা সময় কাটাতেন। মর্গে যাওয়া ছাড়াও চার্লস ডিকেন্সের ছিল আফিমে আসক্তি, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতন। আর্নেস্ট হেমিংওয়ের ছিল মদের প্রতি আসক্তি, কমলকুমার মজুমদারের মতন। মদের ভালোবাসা থেকে তিনি লিখেছেন- যখন আপনি মাতাল, তখন আপনি অনেক বেশি ভদ্র । এটা আপনার মুখ বন্ধ রাখতে সাহায্য করবে। আমেরিকান রোমান্টিক মুভমেন্টের প্রধান ব্যক্তি, অ্যাডগার অ্যালান পো ছিলেন মাদকাসক্ত। হেমিংওয়ের মতো তিনিও দুঃখ-কাতরতা থেকে মুক্ত থাকার জন্য মদ পান শুরু করেন। ব্রিটিশ কবি, রোমান্টিক মুভমেন্টের অন্যতম প্রবক্তা, কুবলা খান ও দ্য রাইম অব দ্য এনসিয়েন্ট মেরিনার এর কবি স্যমুয়েল টেইলর কোলরিজে আফিমে আসক্ত ছিলেন। সেই সময় তিনি আফিমখোর হিসেবে ব্রিটেনে পরিচিত ছিলেন এবং এটা নিয়ে তিনি গর্বও বোধ করতেন। তিনি বলেছেন, কুবলা খান লিখতে গিয়ে আফিমের ঘোর তাঁকে সাহায্য করেছিল। ট্রেজার আইল্যান্ড, দ্য স্ট্রেঞ্জ কেস অব ডা. জ্যাকেল অ্যান্ড মি. হাইড-এর স্রষ্টা স্কটিশ সাহিত্যিক রবার্ট লুইস স্টিভেনসন ছিলেন কোকেনে আসক্ত। তার স্ত্রীর ভাষ্যমতে, তিনি কোকেন নিয়ে করে মাত্র ছয় দিনে ঘোরগ্রস্ত অবস্থায় ৬০ হাজার শব্দ লিখেছিলেন। এর মধ্যে দ্য স্ট্রেঞ্জ কেস অব ডা. জ্যাকেল অ্যান্ড মি. হাইডও লিখেছেন।
.
তিন
১৯১৭ সালে গিয়ম অ্যাপলিনেয়ার “সুররিয়ালিজম” অভিধাটি তৈরি করেছিলেন, যার অর্থ ছিল বাস্তবের অতীত। শব্দটি প্রায় লুফে নেন আঁদ্রে ব্রেতঁ, নতুন একটি আন্দোলন আরম্ভ করার পরিকল্পনা নিয়ে, যে আন্দোলনটি হবে পূর্ববর্তী ডাডাবাদী আন্দোলন থেকে ভিন্ন । ত্রিস্তঁ জারা উদ্ভাবিত ডাডা আন্দোলন থেকে সরে আসার কারণ হল ব্রেতঁ সহ্য করতে পারতেন না ত্রিস্তঁ জারাকে, কেননা কবি-শিল্পী মহলে প্রতিশীল্পের জনক হিসাবে ত্রিস্তঁ জারা খ্যাতি পাচ্ছিলেন। আঁদ্রে ব্রেতঁ সুররিয়ালিজম তত্বটির একমাত্র ব্যাখ্যাকারী হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে আরম্ভ করেন। ১৯১৯ সালে ত্রিস্তঁ জারাকে কিন্তু ব্রেতঁ চিঠি লিখে প্যারিসে আসতে বলেছিলেন । একইভাবে ‘হাংরি’ শব্দটি মলয় রায়চৌধুরী পেয়েছিলেন কবি জিওফ্রে চসার থেকে । এই ‘হাংরি’ শব্দটি নেয়ার জন্য মলয় রায়চৌধুরীকে যেভাবে আক্রমণ করা হয়েছে, তেমন কিছুই করা হয়নি আঁদ্রে ব্রেতঁ ও ত্রিস্তঁ জারা সম্পর্কে । মলয় রায়চৌধুরী হাংরি জেনারেশন আন্দোলন ঘোষণা করেন ১৯৬৫ সালের পয়লা নভেম্বর একটি লিফলেট প্রকাশের মাধ্যমে ।
পরাবাস্তববাদী আন্দোলনে, প্রথম থেকেই, আঁদ্রে ব্রেতঁ’র সঙ্গে অনেক পরাবাস্তববাদীর সদ্ভাব ছিল না, কিন্তু পরাবাস্তববাদ বিশ্লেষণের সময়ে আলোচকরা তাকে বিশেষ গুরুত্ব দেন না । আমরা যদি বাঙালি আলোচকদের কথা চিন্তা করি, তাহলে দেখব যে তাঁরা হাংরি জেনারেশন বা ক্ষুধার্ত আন্দোলন বিশ্লেষণ করার সময়ে হাংরি জেনারেশনের সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে অত্যধিক চিন্তিত, হাংরি আন্দোলনকারীদের সাহিত্য অবদান নিয়ে নয় । ব্যাপারটা বিস্ময়কর নয় । তার কারণ অধিকাংশ আলোচক হাংরি জেনারেশনের সদস্যদের বইপত্র সহজে সংগ্রহ করতে পারেন না এবং দ্বিতীয়ত সাংবাদিক-আলোচকদের কুৎসাবিলাসী প্রবণতা ।
আঁদ্রে ব্রেতঁ তাঁর বন্ধু পল এলুয়ার, বেনিয়ামিন পেরে, মান রে, জাক বারোঁ, রেনে ক্রেভালl, রোবের দেসনস, গিয়র্গে লিমবোর, রোজের ভিত্রাক, জোসেফ দেলতিল, লুই আরাগঁ ও ফিলিপে সুপোকে নিয়ে ১৯১৯ পরাবাস্তববাদ আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন । কিছু
দুই
যাঁরা কবি ও লেখকদের পারস্পরিক অবনিবনাকে গুরুত্ব দিয়েছেন, তাঁরা লেখক-প্রতিস্ব নির্মাণের ব্যাপারটা ভেবে দ্যাখেননি, বিশেষ করে সমাজটির আর্থসামাজিক পৃষ্ঠপটে ও পূর্বের সাহিত্যিক পঠন-পাঠনের প্রভাবে নির্মিত প্রতিস্ব ।
প্রথম ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র ও প্রথম ছোটোগল্পকার পূর্নচন্দ্র থেকে হাল আমলের মফসসলের কথাসাহিত্যিক, প্রান্তিক ও শহুরে গল্পকার কিংবা মেট্রপলিটান ঔপন্যাসিক, তাঁদের লেখক প্রতিস্ব অবিনির্মাণ করলে প্রথম যে উপাদানটি পাওয়া যাবে, তা তাঁদের মাতৃভাষায় এবং অন্যান্য যে ভাষায় তাঁদের দখল আছে, সে ভাষায় পূর্ব প্রজন্মগুলোর সাহত্যিকদের লেখা গল্প-উপন্যাসের পঠন-পাঠনের জমা করা স্মৃতি । ব্যক্তিপ্রতিস্ব নির্মাণে ভাষার অবদান অনস্বীকার্য, কিন্তু লেখক-প্রতিস্ব নির্মাণে ভাষাসাহিত্যের জ্ঞান তথা সাহিত্যের বিশেষ ঝোঁকের প্রতি লেখকের টান, তাঁর লেখনকর্মের আদল আদরা দিশা তাৎপর্য অন্তর্নিহিত-সম্পদ দাপট চৈতন্য অস্তিত্ব আত্ম-উন্মোচন এমনকী তাঁর সাহিত্য চক্রান্তক কলমটির গঠনকারী মূল উপাদান । তাঁদের লেখন-অভিজ্ঞতার মালিকানার বখরা কিন্তু তাঁদের পড়া পূর্বসূরী গল্পকার-ঔপন্যাসিক-দার্শনিকদের প্রাপ্য।
আমি যে প্রতিস্ব-নির্মাণের কথা বলছি তা বাংলা সাহিত্যের এক বিশেষ বাঁকবদলের সময়কার । উল্লেখ্য যে ভারতবর্ষে পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, বেতাল পঞ্চবিংশতি, কথাসরিৎসাগর, বৃহৎকথা, কথামঞ্জরী, দশকুমার চরিত, বাদবদত্তা ইত্যাদি গদ্যে রচিত কথাবস্তুর অতিপ্রাচীন ঐতিহ্য আছে । ইংরেজরা আসার পর, এবং ফলে, বাংলা গদ্যসাহিত্য ও গদ্যে নানা ধরণের সংরূপের উদ্ভব জলবিভাজকের কাজ করেছিল ; আমি সেদিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি । এক নতুন নন্দনক্ষেত্র তৈরি হয়েছিল সাহিত্যের এলাকায়, যে এলাকায় লেখক নামের নির্মিত-প্রতিস্বের মানুষটির লেখনকর্মকে কৌমনিরপেক্ষ ব্যক্তিলক্ষণ হিসেবে নৈতিকতা আর বৈধতা আরোপের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছিল । ফলে লেখনকর্ম বা পাঠবস্তুতে সতত কেন্দ্র দখল করে থাকলেন লেখ-সৃষ্টিকারী ব্যক্তিমালিকটি ।
ইংরেজরা আসার পরই, আর বাংলা কথাসাহিত্যের শুরুতেই যে লেখকরা নির্মিত-প্রতিস্ব নিয়ে লেখন-পরিসরে নেমেছিলেন, তা কিন্তু নয়। লেখন পরিসরে ব্যক্তিনামের লালন, ব্যক্তি-আধিপত্যের ছাপ, ব্যক্তিপ্রসূত রচনাগত মৌলিকতা, ব্যক্তিসৃজনশীলতা ইত্যাদি প্রতর্কগুলো হিন্দু বাঙালির জীবনে প্রবেশ করতে পেরেছিল সেই সময়কার কলকাতায় ইউরোপীয় আলোকপ্রাপ্তির মননবিশ্বটি পাকাপাকি ভাবে থিতু হয়ে বসার পর । ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা, ১৮৩৫ থেকে শিক্ষার বাহন হিসেবে ইংরেজি, তারপর ১৮৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিক্ষিত বাঙালির সমাজে ওই মননবিশ্ব প্রবেশ করতে পেরেছিল। বাংলা ভাষার প্রথম উপন্যাস ‘দুর্গেশনন্দিনী’ প্রকাশিত হয় ১৮৬৫ সালে, লেখক হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্রের মননবিশ্বটি ওই আদরায় নির্মিত হবার পর এবং ফলে, আর একই কারণে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাই পূর্ণচন্দ্র দ্বারা রচিত হলো, ১৮৭৩ সালে, প্রথম বাংলা ছোটোগল্প ‘মধুমতী’ । তার আগে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা এবং ১৮৩১ সালে প্রকাশিত ‘নববাবুবিলাস’ আর ১৮৫৮ সালে প্রকাশিত প্যারীচাঁদ মিত্রের লেখা ‘আলালের ঘরের দুলাল’ পাঠবস্তুগুলোতে ওই মননবিশ্বের ছাপ ছিল না ।
পূর্ণচন্দ্র তাঁর গল্পটিতে নামস্বাক্ষর করেননি । ‘নববাবুবিলাস’ আর ‘আলালের ঘরের দুলাল’ ছদ্মনামে লেখা । নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী তাঁর ‘বাংলা ছোটোগল্প — সংক্ষিপ্ত সমালোচনা’ বইতে জানিয়েছেন যে ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকার সময়কালে ( ১২৮০ থেকে ১৩০৬ বঙ্গাব্দ ) বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় একশ ছাব্বিশটি ছোটোগল্প প্রকাশিত হয়েছিল যেগুলোয় লেখকরা নামস্বাক্ষর করেননি, এমনকী ছদ্মনামও নয় । রচনার সঙ্গে লেখকের নাম দেওয়ার প্রথাটি প্রবর্তন করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রাহ্মধর্মের প্রভাবশালী প্রতিনিধি । সেসময়ে ব্রা্হ্মধর্ম হয়ে উঠেছিল ওই মননবিশ্বের ধারক ও বাহক । নামস্বাক্ষর না-করার প্রক্রিয়াটি থেকে স্পষ্ট যে কথাবস্তুর রচয়িতারা জানতেন না যে লেখকসত্তা বলে কোনো ব্যাপার হয়, এবং লেখকের নামটি সত্তাটিকে বহন করে । কোনও কথাবস্তু যে মেধাস্বত্ত, সে ধারণাটির প্রতিষ্ঠা হতে সময় লেগেছিল । তার কারণ অস্তিত্বের কেন্দ্রে ব্যক্তিমানুষকে স্হাপনের কর্মকাণ্ডটির প্রভাব, যাকে উনিশ শতকের রেনেসঁস বলা হয়, সেই চিন্তাচেতনাকে ছড়িয়ে দেবার জন্য অজস্র নির্মিত-প্রতিস্বের প্রয়োজন ছিল । ইউরোপীয় চিন্তনতন্ত্রটির বাইরে যে নন্দনক্ষেত্রটি রয়ে গেল, জলবিভাজিকার অন্য দিকে, তাকে বটতলা নামে এইজন্য দোষারোপ করা হল যে সেই এলাকায় ব্যক্তিএককগুলো অনির্মিত। জেমস লঙ বললেন বটতলার বইগুলো অশ্লীল ও অশোভন, যার দরুন বাংলার সংস্কৃতি থেকে লোপাট হয়ে গেল বইগুলো ।
ইউরোপ থেকে আনা সাহিত্য-সংরূপগুলোর সংজ্ঞার স্বামীত্ব, তাদের ব্যাখ্যা করার অধিকার, দেশীয়করণের বৈধতা, সেসব বিধিবিধান তত্বায়নের মালিকানা, কথাবস্তুটির উদ্দেশ্যমূলক স্বীকৃতি, চিন্তনতন্ত্রটির অন্তর্গত সংশ্লেষে স্বতঃঅনুমিত ছিল যে, অনির্মিত লেখকপ্রতিস্বের পক্ষে তা অসম্ভব, নিষিদ্ধ, অপ্রবেশ্য, অনধিকার চর্চা । ব্যাপারটা স্বাভাবিক, কেননা যাঁরা সংজ্ঞাগুলো সরবরাহ করছেন, তাঁরাই তো জানবেন যে সেসব সংজ্ঞার মধ্যে কী মালমশলা আছে, আর তলে-তলে কীইবা তাদের ধান্দা । ফলে, কোনও কথাবস্তু যে সংরূপহীন হতে পারে, লেখক-এককটি চিন্তনতন্ত্রে অনির্মিত হতে পারে, রচনাকার তাঁর পাঠবস্তুকে স্হানাংকমুক্ত সমাজপ্রক্রিয়া মনে করতে পারেন, বা নিজেকে বাংলা সাহিত্যের কালরেখার বাইরে মনে করতে পারেন, এই ধরণের ধারণাকে একেবারেই প্রশ্রয় দেয়নি ওই চিন্তনতন্ত্রটি । বর্তমান কালখণ্ডে, আমরা জানি, একজন লোক লেখেন তার কারণ তিনি ‘লেখক হতে চান’ । অথচ লেখক হতে চান না এরকম লোকও তো লেখালিখি করতে পারেন । তাঁরা সাহিত্যসেবক অর্থে লেখক নন, আবার সাহিত্যচর্চাকারী বিশেষ স্হানাংক নির্ণয়-প্রয়াসী না-লেখকও নন । তাঁদের মনে লেখক হওয়া-হওয়ি বলে কোনও সাহিত্য-প্রক্রিয়া থাকে না ।
বহুকাল যাবৎ বিভিন্ন আলোচককে মন্তব্য করতে দেখা গেছে যে, উপন্যাস আর্ট ফর্মটির বঙ্গীয়করণ করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, ছোটোগল্প আর্টফর্মটিকে সম্পূর্ণ দেশজ করে নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, সনেট-তের্জারিমা-ভিলানেলকে এতদ্দেশীয় করেছিলেন প্রমথ চৌধুরী ইত্যাদি । এই যে একটি ভিন্ন ভাষসাহিত্যের সংরূপকে আরেকটি ভাষাসাহিত্যে এনে সংস্হাপন, এর জন্য দ্বিভাষী দক্ষতা এবং সংরূপটি সম্পর্কে গভীর জ্ঞানই যথেষ্ট নয় । যিনি এই কাজটিতে লিপ্ত, তাঁর গ্রাহীক্ষমতা, বহনক্ষমতা ও প্রতিস্হাপন ক্ষমতা থাকা দরকার। অমন ক্ষমতা গড়ে ওঠে জ্ঞান আহরণের মাধ্যমে । আর এই জ্ঞান আহরণ তখনই সম্ভব যখন আ্হরণকারীর লেখক-প্রতিস্বের নির্মাণ ঘটে জ্ঞানটির পরিমণ্ডলে ।
অনির্মিত লেখক-একককে ব্র্যাণ্ডার ম্যাথিউজ প্রণীত ছোটোগল্পের সংজ্ঞার প্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করা যাক । ‘দি ফিলজফি অফ দি শর্ট স্টোরি’ বইতে ম্যাথিউজ বলেছেন, “যাহা কেবলমাত্র গল্প এবং পরিসরে ক্ষুদ্র, তাহাই ছোটোগল্প নহে । ভাবের ঐক্য ছোটোগল্পের পক্ষে অপরিহার্য এবং এইখানেই উপন্যাসের সহিত ইআর পপধান প্রভেদ । ছোটোগল্পে ভাবের ঐকভ আছে, উপন্যাসে নাই । ক্ল্যাসিকাল ফরাসি নাটকের তিনটি ঐক্যই ফরাসি নাটকে আছে ; ইহা একটি ক্ষেত্রে, একটি দিনে, বিশেষ একটি ঘটনা দেখায় । ছোটোগল্পে একটিমাত্র চরিত্র, ঘটনা বা ভাব থাকে, অথবা একটিমাত্র পরিস্হিতির পটভূমিকায় কতকগুলো ভাবের সমাবেশ ঘটে।” এখন, অনির্মিত লেখক-প্রতিস্বের কাছে ‘ভাবের ঐক্য’, ‘ভাবের সমাবেশ’ ‘ক্লসিকাল ফরাসি নাটক’ ইত্যাদি ভাবকল্পগুলো দুর্ভেদ্য থেকে যাবে, এবং ব্যাখ্যার পরও বিমূর্ততা কাটবে না ।
‘অ্যান ইনট্রোডাকশান টু দি স্টাডি অফ লিটারেচার’ বইতে দেয়া ডাবলু. এইচ. হাডসন-এর তৈরি অনুশাসনের প্রেক্ষিতেও ব্যাপারটা বিচার করা যেতে পারে । হাডসন বলেছেন, “ছোটোগল্পে শিল্পকলার মূল্য নির্ধারণের জন্য ‘একক উদ্দেশ্য ও ভাবের ঐক্য’ বজায় আছে কিনা তা দেখা উচিত।” এখানেও প্রশ্ন উঠবে ‘শিল্পকলা’, তার ‘মূল্য নির্ধারণ’ এবং ‘একক উদ্দেশ্য’ ভাবকল্পগুলো নিয়ে । বস্তুত যে চিন্তনতন্ত্রের কথা একটু আগে বলেছি, তার সরবরাহ করা সংজ্ঞায় খাপ খায়নি বলে পূর্ণচন্দ্র চট্টপাধ্যায়ের লেখা ‘মধুমতী’ রচনাটিকে সার্থক ছোটোগল্পের তকমা দেয়া হয়নি । সার্থক ছোটোগল্পের তকমা দেয়া হল ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের লেখা ‘দেনাপাওনা’ রচনাটিকে । ছোটোগল্পের সংজ্ঞাকে গভীরভাবে বুঝতে না পারলে ‘সার্থক’ ছোটোগল্প লেখা সম্ভব ছিল না । সার্থকতা নামের মানদন্ডটি ওই চিন্তনতন্ত্রের ফসল । বর্তমান কালখণ্ডে ওই চিন্তনতন্ত্র বাতিল হয়ে গেছে, সেটা ভিন্ন প্রসঙ্গ ।
ওপরের কথাগুলো এইজন্য বলতে হল যে অবনী ধর, যাঁর চোদ্দটি গদ্য নিয়ে ‘ওয়ান সট’ বইটি প্রকাশিত হয়েছিল, তিনি ছোটোগল্প-লেখক বা গল্পকার হওয়া-হওয়ি অবস্হান থেকে সেগুলো লেখেননি, এবং তাঁর লেখক-প্রতিস্বটি ছিল অনির্মিত । ১৯৬৯ থেকে ২০০৩ পর্যন্ত, এই কালখণ্ডে তিনি এও চোদ্দটি গদ্যই লিখেছিলেন। ১৯৭৫ সালের পর তিনি লেখালিখি ছেড়ে দিয়েছিলেন । হাংরি আন্দোলনের সময়ে তাঁর সঙ্গে আমার একবারই দেখা হয়েছিল, অশোকনগরে, কিন্তু তখনও তিনি লেখালিখি আরম্ভ করেননি, যদিও তিনি নিজের জীবনের এই ঘটনাগুলো শোনাতে ভালোবাসতেন । তাঁর কথনভঙ্গিমা ও জীবননাট্যের ঘটনা থেকে স্পষ্ট ছিল যে কথাবস্তুর পরিসরটি সেই সময়ের সাহিত্যিক ডিসকোর্স এবং কাউন্টার-ডিসকোর্স থেকে একেবারে আলাদা, এমনকী হাংরি আন্দোলনের গল্পকার-ঔপন্যাসিক থেকেও আলাদা । ১৯৯৪ সালে কলকাতায় ফিরে জানতে পারি যে অবনী ধরের রচনাগুলো নিয়ে বই বের করার উৎসাহ কোনও হাংরি আন্দোলনকারী দেখাননি । আমি শর্মী পাণ্ডেকে অনুরোধ করি যে অবনী ধরের গদ্যগুলো নিয়ে একটা সংগ্রহ ওদের শিলালিপী প্রকাশনী থেকে বের করতে । শর্মী আর ওর স্বামী শুভঙ্কর দাশ তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে যায় আর আমাকে একটা ভূমিকা লিখে দিতে বলে । এই সময়ে অবনী ধরের সঙ্গে আমার বেশ কয়েকবার সাক্ষাৎ ঘটে আর ওনার জীবন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে ফেলি । অবনী ধর জন্মেছিলেন ১৯৩৪ সালে, তখনকার পূর্ববঙ্গের মাদারিপুর জেলার কালাকিনি থানার পাঙাশিয়া গ্রামে. তাঁর মামার বাড়িতে । মারা যান ২০০৭ সালে, অশোকনগরে । তাঁর বাবা বঙ্কিমচন্দ্র ধর ( ১৯০৫ ) ওই জেলার মাইচপাড়া গ্রামের নিবাসী ছিলেন, সাত ভাইয়ের সবচেয়ে ছোট ; বঙ্কিমচন্দ্র ম্যাট্রিক পাশ করেছিলেন, কিন্তু কখনও কোনও চাকরি বা ব্যবসা করেননি ; স্বাদেশী আন্দোলনে যোগ দেবার কারণে কয়েকমাসের জেল হয়েছিল তাঁর । বঙ্কিমচন্দ্র তখনকার দিনের ম্যাট্রিক পাশ ছিলেন, অর্থাৎ যে চিন্তনতন্ত্রের কথা একটু আগে বলেছি, তার মননবিশ্বে অবনী ধরের প্রতিস্বনির্মাণের সুযোগটি গড়ে ওঠার সম্ভাবনা ছিল, বিশেষ করে অবনী ধর যখন তাঁর বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান ।
অবনী ধরের বয়স যখন এক বছর, তখন তাঁর বাবা বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে, তাঁর মা লাবণ্য ধর ( ১৯১৫ – ১৯৭৭ ) , আর ঠাকুমাকে নিজেদের ভাগ্যের ওপরে ছেড়ে দিয়ে, অন্য এক তরুণীর সঙ্গে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, এবং বাকি জীবন বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর সঙ্গিনী বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীরূপে ভিক্ষা করে চালিয়েছিলেন । যদিও বঙ্কিমচন্দ্র মারা যান ১৯৬২ সালে, তাঁর মৃত্যুর খবর অবনীরা পান ১৯৭২ সালে । ততোদিন তাঁর মা শাঁখা-সিঁদুর পরতেন । অবনী ধরের লেখক-প্রতিস্ব প্রাগুক্ত চিন্তনতন্ত্রের পরিসরে যদি গড়ে উঠত, তাহলে তিনি এই ট্র্যাজেডির মুহূর্তটি নিয়ে একটি কথাবস্তু তৈরি করতে পারতেন, কেননা ইউরোপীয় সাহিত্যে গ্রিসের সময় থেকে ব্যক্তি-এককের ট্র্যাজেডিটি লেখকত্ব প্রতিষ্ঠার অন্যতম উপাদান ছিল, যা খ্রিস্টের নৃশংস হত্যা ও আত্মবলিদানের প্রতীকি অতিকথার প্রচার-প্রসারের কারণে সাহিত্যের নন্দনক্ষেত্রটিকে দখল করে নিতে পেরেছিল । তাছাড়া বাইবেলোক্ত “আরিজিনাল সিন” বা প্রথম পাপের পতনযন্ত্রণাকে সর্বজনীন নৈতিক-দার্শনিক বনেদে পালটে ফেলার জন্যেও জরুরি ছিল ইউরোপীয় সাহিত্যের পাতায় পাতায় ব্যক্তি-ট্র্যাজেডির উপস্হিতি ।
অবনী ধরের জীবনে বহুবার বহুরকম ট্র্যাজেডি সংঘটন দেখা গেছে, কিন্তু সেসব অভিজ্ঞতার সরাসরি মালিকানা সত্তেও তিনি সংঘটন-মুহূর্ত বা ক্লাইম্যক্স বা হুইপক্র্যাক এনডিং প্রয়োগ করে কথাবস্তুকে ঔপনিবেশিক সাহিত্য-অনুশাসন ও হেলেনিক মূল্যবোধের অন্তর্ভুক্ত করেননি । প্রকৃত প্রস্তাবে কথাবস্তুগুলো গড়ে উঠেছে ঔপনিবেশিক সাহিত্য-মূল্যবোধের আওতার বাইরে । প্রসঙ্গত, যে সময়ে অবনী ধর তাঁর প্রথম পর্বের গদ্যগুলো লিখেছিলেন, সেসময়ে মান্যতাপ্রাপ্ত বাংলা ছোটো গল্পকাররা ইউরোপীয় সাহিত্যের অনুশাসন মোতাবেক, বিষণ্ণতা, পারক্য, প্রেমের বিকার, মৃত্যুপ্রবণতা, নিঃসঙ্গতার বেদনা,শহুরে যৌনতা ইত্যাদির চর্চা করছিলেন ।
বাবা বঙ্কিমচন্দ্র তাঁদের একা ফেলে নিরুদ্দেশ হবার কারণে বছর পাঁচেক অন্নকষ্টে ভোগার পর তখনকার বিহারে ( এখন ঝাড়খণ্ড ) মধুপুরনিবাসী অবনীর ‘বুড়োমা’ অর্থাৎ তাঁর ঠাকুর্দার ভাইয়ের স্ত্রী, অবনী ও তাঁর মাকে দেখাসোনার জন্য, ও নিজের বার্ধক্যে দেখভালের জন্য, সেখানে নিয়ে গেলেন । যদিও অবনীর জ্যাঠামশাবরা, প্রথম দুজন ডাক্তার, ততীয়জন উকিল, চতুর্থজন স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন, এবং পঞ্চম ও ষষ্ঠ যথাক্রমে দেওঘর ও মধুপুরে আশ্রম বসিয়ে তার মোহন্ত ছিলেন, অবনীর পড়াশুনার এবং স্কুলে ভর্তি হবার সুরাহা হলো না । বুড়োমার আশ্রয়ে অবনী ও তাঁর মায়ের অন্ন সমস্যার সমাধান হলেও, শিক্ষাপ্রাপ্তির সুযোগ ঘটল না । স্কুলে ভর্তির জন্য অবনীকে কলকাতার চেতলায় মামারবাড়ি যেতে হলো । প্রবাদবাক্যের মামার বাড়ির আবদারের বদলে অহরহ দুর্ব্যাবহার জোটায়, ১৯৫০ সালের পয়লা অক্টোবর, কাউকে না জানিয়ে, স্কুল থেকে পালিয়ে, অবনী চলে গেলেন মার্চেন্ট নেভিতে, খালাসির কাজ নিয়ে । তখন তাঁর ষোলো বছর বয়স ।
এই সময়ের অভিজ্ঞতাগুলো অবনী সংগ্রহ করেন জাহাজে খালাসির কাজ করার সময়ে, বিভিন্ন দেশের বন্দর-শহরে, ইউরোপ তখনও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভাঙন কাটিয়ে উঠতে পারেনি । বস্তুত তাঁর খালাসিপর্বের কথাবস্তুগুলো, কথনভঙ্গীর অন্তর্গত আহ্লাদময়তার কারণে, সুখশ্রাব্য ও কৌতূহলোদ্দীপক ছিল, যে গল্পগুলো বাসুদেব দাশগুপ্তকে তিনি শোনাতেন । অনেকে মনে করেন বাসুদেব দাশগুপ্তের গল্পগুলোর উৎস হলো অবনী ধরের অভিজ্ঞতা । লেখালিখি না করেও অবনী ধর তাঁর জীবনযাপনের কারণে নিজেকে হাংরি আন্দোলনকারী মনে করতেন । হাংরি আন্দোলনকারীদের সঙ্গে খালাসিটোলায় ঢুঁ মারতেন । বাসুদেব দাশগুপ্ত ও শৈলেশ্বর ঘোষের প্ররোচনায় সোনাগাছির যৌনকর্মী বেবি, মীরা এবং দীপ্তির সঙ্গে নৈকট্য গড়ে ফেলেছিলেন ।
হাংরি আন্দোলনের সময়ে, উৎসাহদানকারী সম্পাদক ও স্তাবকদলের অভাবে, এবং অবনী ধরের সাহিত্যিক উচ্চাকাঙ্খার অনুপস্হিতিতে, তাঁর বলা কাহিনিগুলো লিখিত পাঠবস্তুর আকার নিতে পারেনি । জরুরি অবস্হার শেষে সারা পশ্চিমবাংলা জুড়ে লিটল ম্যাগাজিন বিস্ফোরণ ঘটলেও, সম্পাদকরা অবনীর গদ্য সম্পর্কে আগ্রহী হননি, মূলত তাঁর কথনভঙ্গীর ও রচনাকাঠামো বিদ্যায়তনিক সংরূপ বহির্ভূত ছিল বলে । একজন খালাসির গদ্যসন্দর্ভে যে যাযাবরতার নিবাস, যার উপকরণগুলো যাত্রাপথের খুদে অনির্ণেয়তায় তাৎপর্যময়, যার বিন্যাসে ভাসমান পরিভ্রমণের অনুন্মোচিত বাচন, স্নায়ুভাষায় রচিত সেরকম স্বতঃজাত কৃৎপ্রকরণ, স্বীকৃতি পায়নি লিটল ম্যাগাজিন স্তরেও । যেহেতু অবনীর পাঠবস্তু আত্মমগ্নতাকে অতিক্রম করে যায়, এবং তাঁর বাকব্যঞ্জনা বদ্ধসমাপ্তির কাঠামোটাকেই উপহাস করে, প্রধাগত আলোচকদের দৃষ্টিও তিনি আকর্ষণ করতে পারেননি ।
অবনীর ও তাঁর আত্মীয় পরিজনের পরিবারে নিরুদ্দিষ্ট, সাধু, সন্ন্যাসী, মোহন্ত, ভিখারি-বৈষ্ণব, বাউল ইত্যাদির পূর্বেতিহাস থাকার কারণে অবনীর ভবিষ্যৎ নিয়ে তাঁর মা চিন্তিত ছিলেন । বয়ঃসন্ধি অতিক্রান্ত সন্ধিক্ষণে তাঁর ছেলে হয়তো কোনও বন্দরশহর থেকে বিদেশিনী বিয়ে করে বা না-করে সঙ্গে এনে একদিন হাজির হবেন, এমন দুশ্চিন্তাও লাবণ্য ধরের ছিল । ছেলের চরিত্রে অভিজ্ঞতাজনিত পার্থক্যও তিনি লক্ষ্য করে থাকবেন । তিনি অবনীকে বললেন জাহাজের চাকরি ছেড়ে বাড়ি ফিরে আসতে । খালাসির চাকরি ছেড়ে ১৯৫৫ সালে ফিরে এলেন অবনী । বুড়োমা মারা যেতে তাঁর মা মধুপুরে একা হয়ে পড়েছিলেন । অবনী দেশে ফিরে চেতলার একটা বস্তিঘরে, মামার বাড়ির কাছে, বাসা ভাড়া নিয়ে মাকে মধুপুর থেকে নিয়ে এলেন । ১৯৫৫ থেকে ১৯৬৩, এই আট বছর টাকা রোজগারের জন্য নানা রকম জীবিকার অভিজ্ঞতা হলো অবনীর — ক্রেন-ড্রেজার-ডাম্পার অপারেটার, লরি-ট্যাকসি-প্রায়ভেট মোটরগাড়ি চালক, রেলওয়ে ক্যাটারিঙের বেয়ারা, কোককয়লা ফেরি, ঠোঙা ও প্যাকেট তৈরি, পোস্টার-ফেস্টুন লেখা ইত্যাদি, অসংগঠিত শ্রমিকের জন্য যে-ধরণের কাজ পাওয়া যায় সবই করলেন । ১৯৬২ সালে অবনীর মা পাত্রী নির্বাচন করে সাধনার সঙ্গে তাঁর বি্য়ে দেন ।
অবনী তাঁর সংসার ইতিমধ্যে চেতলা থেকে নতুন গড়ে-ওঠা উদ্বাস্তু পুনর্বাসন কলোনি অশোকনগরে তুলে নিয়ে যান । তখন সেখানে স্হানীয় স্বায়ত্বশাসনের পরিকাঠামো বিশেষ ছিল না । তিনি নবতর অভিজ্ঞতার সামনে পড়লেন অশোকনগরে । তিনি এও দেখলেন যে, যাঁদের মাঝে তিনি বসবাস করতে এলেন, তাঁরা পপতিদিনকার মূর্ত নাগরিক অসুবিধা ও জাগতিক দুঃখকষ্টে ও অভাব প্রতিকারের বদলে সোভিয়েত রাষ্ট্র, চিন, ভিয়েৎনাম, কিউবা, আমেরিকা, দিল্লী ইত্যাদি সুদূরবর্তী বিমূর্ত অদরকারি তর্কাতর্কিতে সময় ও ক্ষমতা অপচয় অপচয় করে আনন্দ পান । অর্থাৎ সুপ্রাইণ্ডিভিজুয়াল বা অধিব্যক্তিক ম্যাক্রোলেভেল ভাবুকদের পশ্চিমবাংলার মাটিপৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্কহীন তৎপরতার প্রেক্ষিতে, তাঁর মাইক্রোলেভেল খালাসিত্ব তাঁকে কল্যাণকামীতার স্বাভাবিক সনাতন মূল্যবোধে হায়ারার্কিবর্জিত করে রেখেছিল, এবং সেই ভূমিজ প্রবৃত্তিকে অবনী ধর কাজে লাগালেন ।
তিনি এবং আরও কয়েকজন মিলে, বিশেষ করে শিক্ষক সমর ঘোষ, অশোকনগরে ডাকঘর বসানো, পৌরসভা গঠন, অসামাজিক কাজকারবার বন্ধ ইত্যাদির উদ্যোগ নিলেন । উদ্যোগটিকে কন্ঠস্বর দেবার জন্য, এবং তাঁদের অভাব-অভিযোগ যাতে কর্তাব্যক্তিদের কানে পৌঁছোয়, ১৯৬৪ সালে পপকাশ করা আরম্ভ করলেন ‘অশোকনগর বার্তা’ নামে একটি পাক্ষিক সংবাদপত্র, যেটি ছিল ওই অঞ্চলের প্রথম পঞ্জিকৃত সংবাদপত্র । পত্রিকাটির আয়ু ছিল তিন বছর, সম্ভবত যথেষ্ট । পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত থাকলেও, নিজের অভিজ্ঞতাকে কথাবস্তুতে রূপান্তরিত করে ছাপাবার কথা তাঁর মনে আসেনি কখনও ; পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত অন্যেরাও তাঁর মুখে ঘটনা শুনেও তাঁকে লিখতে বলেননি । সম্ভবত সমাজচিন্তনকে আত্মসাৎ করে ব্যক্তি-ক্রিয়াকরণের চিন্তা-পরিসর লালিত হবার মতো পৃথকত্ববোধ জাগার সুযোগ বা মনস্হিতি তাঁর হয়নি । ১৯৬৩ সাল থেকে চাকুরিহীন অবনীর কাছে আপনা থেকেই পরিত্যক্ত হয়েছিল ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার দর্শন ।
অবনী ধরের কথাবস্তুগুলোকে দুটি পর্বে চি্হ্ণিত করা যায় । প্রথম পর্বটি ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় পর্বটি ২০০০ সালের পর । মাঝে লেখা ছেড়ে দিয়েছিলেন । প্রথম পর্বে তিনি ছিলেন অর্থস্রোতহীন এবং কোনও সাহিত্যিক স্বকীয়তা আনার প্রয়াস করেননি । তা আপনা থেকে হয়ে গিয়েছিল তাঁর অনির্মিত লেখক-প্রতিস্বের কারণে । অবনী ধরের ডিসকোর্স, কখনও খালাসির, কখনও বা অসংগঠিত শ্রমিক বা কর্মহীনের, ভূপ্রকৃতির উথ্থানভূমিলব্ধ, স্হানিক, অবিমিশ্র, মুক্ত, যৌগিক, বর্ণিল, অনুভূমিক, প্রতিসংস্হাপিত, কৌমনিষ্ঠ এবং অতিজ্ঞাপনমূলক । প্রথম লেখাটি, ‘আমার দুঃখী মা’ রচনার পর তিনি তা লাবণ্য ধরকেই পড়ে শুনিয়েছিলেন । স্তম্ভিত মা কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর. বলেছিলেন, ‘সত্য কথাই ল্যাখছস।’
দ্বিতীয় পর্বের শুরু ২০০০ সালে । এই পর্বে অবনীর গদ্য-কাঠামোয় কয়েকটি কারণে সাইত্যিকতা এসে গেছে । তাঁর স্ত্রী, আরও কয়েকজন সহকর্মীর সঙ্গে একজোট হয়ে মামলা করে ১৯৯০ সালে চাকরি পাবার পর অবনীর আর্থিক অনিশ্চয়তা কাটে । তাঁর মেয়ে ইতিহাসে স্নাতকোত্তর ও বি এড এবং ছেলে বি এ পাশ করেন । অর্থাৎ প্রথম পর্বের জ্ঞান পরিমণ্ডলটি, তাঁর মেয়ে ও ছেলের প্রভাবে ক্রমশ অপসারিত হয়ে বাড়ির মধ্যে একটি ভিন্ন, যা অবনীর কাছে তুলনামূলকভাবে উচ্চতর ঠেকে থাকবে, জ্ঞানপরিমণ্ডলের প্রবেশ ঘটিয়েছে । তৃতীয়ত, তাঁর প্রথম পর্বের রচনাগুলো, অন্তত কিছু সাহিত্যপাঠকের, হাতে গোনা হলেও, দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকবে, যাঁদের পাঠ-প্রতিক্রিয়ায় তিনি উৎসাহিত হয়ে থাকবেন গদ্যগুলোকে একটি সাহিত্যিক আদল-আদরা দেবার । দ্বিতীয় পর্বের কথাবস্তুগুলোর গদ্যবিন্যাসে ধরা পড়ে যে প্রথাবাহিত গদ্যসাহিত্যের সঙ্গে, যেগুলো তাঁর ছেলে-মেয়ে নিজেরা পড়ার জন্য বাড়িতে এনে থাকবেন, তাঁর যোগাযোগ ঘটেছে । অবনী নিজে চেষ্টা করলেও, এই বয়সে পৌঁছে, তাঁর পক্ষে মুকুরবিম্ব গড়া সম্ভবপর হয়নি, এবং তাঁর অপরত্ববোধ ও সাহিত্যিক অপরত্ব মুছে যায়নি । প্রথম ও দ্বিতীয়, দুটি পর্বেই, তাঁর জীবনজিজ্ঞাসা তাড়িত হয়েছে অপরত্ববোধের অবস্হাননজনিত বিপর্যয় দ্বারা। আর কোনো বাঙালি সাহিত্যিকের কথাবস্তুতে, অপরত্ববোধের মাত্রাগুলোকে, অবনীর মতো করে ইতোপূর্বে উপস্হাপন করতে দেখা যায়নি । তাঁর মস্তিষ্কে আতিথ্য নেয়া কথাকারটি নিজেরই স্মৃতির ঐতিহাসিক হিসেবে অবনীর সামনে উদয় হয়েছে কখনও-সখনও, যিনি অতীতকে বাঁচিয়ে তুলতে চেষ্টা করছেন না বা অতীতে বেঁচে থাকার কথা বলছেন না ; আসলে কথাকার ওই দূরবর্তী এবং নিকট অতীতের লোপাট হয়ে যাওয়া ও তাকে বাগে আনার বাচনক্রীড়ায় অংশগ্রহণকারীরূপে ‘অপর প্রতিসন্দর্ভের’ সতর্কতাগুলো জাহির করছেন ।
দুই
উত্তরবঙ্গে হাংরি জেনারেশনের প্রসার সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে, হাংরি পত্রিকা ‘কনসেনট্রেশন ক্যাম্প’ এর সম্পাদক অলোক গোস্বামী এই কথাগুলো লিখেছিলেন, তা থেকে অবনিবনার যৎসামান্য আইডিয়া হবে, কিন্তু এই অবনিবনার সঙ্গে পরাবাস্তববাদীদের নিজেদের অবনিবনারে যথেষ্ট মিল আছে :-
“নব্বুই দশকে সদ্য প্রকাশিত কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প বগলে নিয়ে এক ঠা ঠা দুপুরে আমি হাজির হয়েছিলাম শৈলেশ্বরের বাড়ির গেটে। একা। ইচ্ছে ছিল শৈলেশ্বরের সঙ্গে মুখোমুখি বসে যাবতীয় ভুল বোঝাবুঝি নিয়ে খোলাখুলি কথা বলবো। যেহেতু স্মরণে ছিল শৈলেশ্বরের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের স্মৃতি তাই আস্থা ছিল শৈলেশ্বরের প্রজ্ঞা,ব্যক্তিত্ব,যুক্তিবোধ তথা ভদ্রতাবোধের ওপর। দৃঢ় বিশ্বাস ছিল শৈলেশ্বর আমাদের ভুলগুলো ধরিয়ে দেবেন এবং যৌথ আলোচনাই পারবে সব ভুল বোঝাবুঝি মিটিয়ে নতুন উদ্যমে একসাথে পথ চলা শুরু করতে। কিন্তু দুভার্গ্য বশতঃ তেমন কিছু ঘটলো না। বেল বাজাতেই গেটের ওপারে শৈলেশ্বর। আমাকে দেখেই ভ্রূ কুঁচকে ফেললেন।
--কী চাই!
মিনমিন করে বললাম, আপনার সঙ্গে কথা বলবো।
--কে আপনি?
এক এবং দুই নম্বর প্রশ্নের ভুল অবস্থান দেখে হাসি পাওয়া সত্বেও চেপে গিয়ে নাম বললাম।
--কি কথা?
--গেটটা না খুললে কথা বলি কিভাবে!
--কোনো কথার প্রয়োজন নেই। চলে যান।
--এভাবে কথা বলছেন কেন?
--যা বলছি ঠিক বলছি। যান। নাহলে কিন্তু প্রতিবেশীদের ডাকতে বাধ্য হবো।
এরপর স্বাভাবিক কারণেই খানিকটা ভয় পেয়েছিলাম কারণ আমার চেহারাটা যেরকম তাতে শৈলেশ্বর যদি একবার ডাকাত, ডাকাত বলে চেঁচিয়ে ওঠেন তাহলে হয়ত জান নিয়ে ফেরার সুযোগ পাবো না। তবে 'ছেলেধরা' বলে চেল্লালে ভয় পেতাম না। সমকামিতার দোষ না থাকায় নির্ঘাত রুখে দাঁড়াতাম।
ভয় পাচ্ছি অথচ চলেও যেতে পারছি না। সিদ্ধান্তে পৌঁছতে গেলে আরও খানিকটা জানা বোঝা জরুরি।
--ঠিক আছে, চলে যাচ্ছি। তবে পত্রিকার নতুন সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে সেটা রাখুন।
এগিয়ে আসতে গিয়েও থমকে দাঁড়ালেন শৈলেশ্বর।
--কোন পত্রিকা?
--কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প।
--নেব না। যান।
এরপর আর দাঁড়াইনি। দাঁড়ানোর প্রয়োজনও ছিল না। ততক্ষণে বুঝে ফেলেছি ব্যক্তি শৈলেশ্বর ঘোষকে চিনতে ভুল হয়নি আমাদের। আর এই সমঝদারি এতটাই তৃপ্তি দিয়েছিল যে অপমানবোধ স্পর্শ করারই সুযোগ পায়নি।”
শৈলেশ্বর ঘোষের হয়তো মনে হয়েছিল যে কলকাতায় তিনি হাংরি আন্দোলনের যে কেন্দ্র গড়ে তুলতে চাইছেন তাতে ফাটল ধরাবার চেষ্টা করা হচ্ছে । তাঁর আচরণ ছিল হুবহু আঁদ্রে ব্রেতঁর মতন । পরাবাস্তববাদ আন্দোলনে আঁদ্রে ব্রেতঁর সঙ্গে অনেকের সম্পর্ক ভালো ছিল না, দল বহুবার ভাগাভাগি হয়েছিল, অথচ সেসব নিয়ে বাঙালি আলোচকরা তেমন উৎসাহিত নন, যতোটা হাংরি আন্দোলনের দল-ভাগাভাগি নিয়ে । ইংরেজিতে মৈত্রেয়ী ভট্টাচার্য চৌধুরী হাংরি আন্দোলন নিয়ে ‘দি হাংরিয়ালিস্টস’ নামে একটি বই লিখেছেন, পেঙ্গুইন র্যাণ্ডাম হাউস থেকে প্রকাশিত । সেই বইটি বাংলা পত্রপত্রিকায় আলোচিত হল না ।
আনন্দবাজার পত্রিকায় ১৬ জুন ২০১৩ তারিখে গৌতম চক্রবর্তী হাংরি আন্দোলন সম্পর্কে এই কথাগুলো লিখেছিলেন ; তাতেও রয়েছে টিটকিরি যা তিনি পরাবাস্তববাদীদের সম্পর্কে কখনও বলেছেন কিনা জানি না । উনি লিখেছিলেন :
“মানুষ, ঈশ্বর, গণতন্ত্র ও বিজ্ঞান পরাজিত হয়ে গেছে। কবিতা এখন একমাত্র আশ্রয়।... এখন কবিতা রচিত হয় অর্গ্যাজমের মতো স্বতঃস্ফূর্তিতে।
১৯৬২ সালে এই ভাষাতেই কলেজ স্ট্রিট কফি হাউস থেকে খালাসিটোলা, বারদুয়ারি অবধি সর্বত্র গোপন বিপ্লবী আন্দোলনের ব্লু প্রিন্টের মতো ছড়িয়ে পড়ে একটি ম্যানিফেস্টো। ২৬৯ নেতাজি সুভাষ রোড, হাওড়া থেকে প্রকাশিত এই ম্যানিফেস্টোর ওপরে লেখা হাংরি জেনারেশন। নীচের লাইনে তিনটি নাম। স্রষ্টা: মলয় রায়চৌধুরী। নেতৃত্ব: শক্তি চট্টোপাধ্যায়। সম্পাদনা: দেবী রায়।
তখনও কলেজ স্ট্রিটের বাতাসে আসেনি বারুদের গন্ধ, দেওয়ালে লেখা হয়নি ‘সত্তরের দশক মুক্তির দশক’। কিন্তু পঞ্চাশ পেরিয়ে-যাওয়া এই ম্যানিফেস্টোর গুরুত্ব অন্যত্র। এর আগে ‘ভারতী’, ‘কবিতা’, ‘কৃত্তিবাস’, ‘শতভিষা’ অনেক কবিতার কাগজ ছিল, সেগুলি ঘিরে কবিরা সংঘবদ্ধও হতেন। কিন্তু এই ভাবে সাইক্লোস্টাইল-করা ম্যানিফেস্টো আগে কখনও ছড়ায়নি বাংলা কবিতা।
ওটি হাংরি আন্দোলনের দ্বিতীয় ম্যানিফেস্টো। প্রথম ম্যানিফেস্টোটি বেরিয়েছিল তার কয়েক মাস আগে, ১৯৬১ সালের নভেম্বর মাসে। ইংরেজিতে লেখা সেই ম্যানিফেস্টো জানায়, কবিতা সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যায় না, বিভ্রমের বাগানে পুনরায় বৃক্ষরোপণ করে না। ‘Poetry is no more a civilizing manoeuvre, a replanting of bamboozled gardens.’ বিশ্বায়নের ঢের আগে ইংরেজি ভাষাতেই প্রথম ম্যানিফেস্টো লিখেছিলেন হাংরি কবিরা। কারণ, পটনার বাসিন্দা মলয় রায়চৌধুরী ম্যানিফেস্টোটি লিখেছিলেন। পটনায় বাংলা ছাপাখানা ছিল না, ফলে ইংরেজি।
দুটি ম্যানিফেস্টোতেই শেষ হল না ইতিহাস। হাংরি আসলে সেই আন্দোলন, যার কোনও কেন্দ্র নেই। ফলে শহরে, মফস্সলে যে কোনও কবিই বের করতে পারেন তাঁর বুলেটিন। ১৯৬৮ সালে শৈলেশ্বর ঘোষ তাঁর ‘মুক্ত কবিতার ইসতাহার’-এ ছাপিয়ে দিলেন ‘সমস্ত ভন্ডামির চেহারা মেলে ধরা’, ‘শিল্প নামক তথাকথিত ভূষিমালে বিশ্বাস না করা’, ‘প্রতিষ্ঠানকে ঘৃণা করা’, ‘সভ্যতার নোনা পলেস্তারা মুখ থেকে তুলে ফেলা’ ইত্যাদি ২৮টি প্রতিজ্ঞা। পরে বন্ধুদের মধ্যে ঝগড়া বাধবে। মলয় ব্যাংকের চাকরি নিয়ে বাইরে চলে যাবেন। শৈলেশ্বর, সুবো আচার্য এবং প্রদীপ চৌধুরীরা বলবেন, ‘মলয় বুর্জোয়া সুখ ও সিকিয়োরিটির লোভে আন্দোলন ছেড়ে চলে গিয়েছে।’কী রকম লিখতেন হাংরিরা? বছর দুয়েক আগে সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের ‘বাইশে শ্রাবণ’ ছবিতে গৌতম ঘোষের চরিত্রটি লেখা হয়েছিল হাংরি কবিদের আদলে।
‘জেগে ওঠে পুরুষাঙ্গ নেশার জন্য হাড় মাস রক্ত ঘিলু শুরু করে কান্নাকাটি
মনের বৃন্দাবনে পাড়াতুতো দিদি বোন বউদিদের সঙ্গে শুরু হয় পরকীয়া প্রেম’,
লিখেছিলেন অকালপ্রয়াত ফালগুনী রায়। র্যাঁবো, উইলিয়াম বারোজ এবং হেনরি মিলারের উদাহরণ বারে বারেই টেনেছেন হাংরিরা। ঘটনা, এঁরা যত না ভাল কবিতা লিখেছেন, তার চেয়েও বেশি ঝগড়া করেছেন। এবং তার চেয়েও বেশি বার গাঁজা, এলএসডি, মেস্কালিন আর অ্যাম্ফিটোমাইন ট্রিপে গিয়েছেন।
অতএব, সাররিয়ালিজ্ম বা অন্য শিল্প আন্দোলনের মতো বাঙালি কবিদের ম্যানিফেস্টোটি কোনও দিন গুরুত্বপূর্ণ হয়নি। কিন্তু ‘হাংরি’রা আজও মিথ। এক সময় ‘মুখোশ খুলে ফেলুন’ বলে তৎকালীন মন্ত্রী, আমলা, সম্পাদকদের বাড়িতে ডাকযোগে তাঁরা মুখোশ পাঠিয়ে দিয়েছেন। আবার এক সময় ‘প্রচন্ড বৈদ্যুতিক ছুতার’ কবিতাটি লেখার জন্য অশ্লীলতার মামলা হল মলয় রায়চৌধুরীর বিরুদ্ধে। উৎপলকুমার বসু, সুবিমল বসাকের বিরুদ্ধে জারি হল গ্রেফতারি পরোয়ানা।
রাষ্ট্র ও আদালত কী ভাবে কবিতাকে দেখে, সেই প্রতর্কে ঢুকতে হলে ১৯৬৫ সালে মলয় রায়চৌধুরীর বিরুদ্ধে মামলাটি সম্পর্কে জানা জরুরি। শক্তি চট্টোপাধ্যায় কাঠগড়ায় উঠেছেন মলয়ের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে। পাবলিক প্রসিকিউটরের জিজ্ঞাসা, ‘প্রচন্ড বৈদ্যুতিক ছুতার’ কবিতাটা পড়ে আপনার কী মনে হয়েছে?
শক্তি: ভাল লাগেনি।
প্রসিকিউটর: অবসিন কি? ভাল লাগেনি বলতে আপনি কী বোঝাতে চাইছেন?
শক্তি: ভাল লাগেনি মানে জাস্ট ভাল লাগেনি। কোনও কবিতা পড়তে ভাল লাগে, আবার কোনওটা ভাল লাগে না।
শক্তি সাক্ষ্য দিয়েছিলেন মলয়ের বিরুদ্ধে। কয়েক মাস পরে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় মলয়ের সমর্থনে...
প্রসিকিউটর: কবিতাটা কি অশ্লীল মনে হচ্ছে?
সুনীল: কই, না তো। আমার তো বেশ ভাল লাগছে। বেশ ভাল লিখেছে।
প্রসিকিউটর: আপনার শরীরে বা মনে খারাপ কিছু ঘটছে?
সুনীল: না, তা কেন হবে? কবিতা পড়লে সে সব কিছু হয় না।
একই মামলায় শক্তি ও সুনীল পরস্পরের বিরুদ্ধে। তার চেয়েও বড় কথা, ’৬৫ সালে এই সাক্ষ্য দেওয়ার আগের বছরই সুনীল আইওয়া থেকে মলয়কে বেশ কড়া একটি চিঠি দিয়েছিলেন, ‘লেখার বদলে আন্দোলন ও হাঙ্গামা করার দিকেই তোমার ঝোঁক বেশি। রাত্রে তোমার ঘুম হয় তো? মনে হয়, খুব একটা শর্টকাট খ্যাতি পাবার লোভ তোমার।’ ব্যক্তিগত চিঠিতে অনুজপ্রতিম মলয়কে ধমকাচ্ছেন, কিন্তু আদালতে তাঁর পাশে গিয়েই দাঁড়াচ্ছেন। সম্ভবত, বন্ধু-শত্রু নির্বিশেষে অনুজ কবিদের কাছে সুনীলের ‘সুনীলদা’ হয়ে ওঠা হাংরি মামলা থেকেই। প্রবাদপ্রতিম কৃত্তিবাসী বন্ধুত্বের নীচে যে কত চোরাবালি ছিল, তা বোঝা যায় উৎপলকুমার বসুকে লেখা সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের একটি চিঠি থেকে, ‘প্রিয় উৎপল, একদিন আসুন।...আপনি তো আর শক্তির মতো ধান্দায় ঘোরেন না।’
তা হলে কি হাংরি আন্দোলন বাংলা সাহিত্যে প্রভাবহীন, শুধুই কেচ্ছাদার জমজমাট এক পাদটীকা? দুটি কথা। হাংরিদের প্রভাবেই কবিতা-সংক্রান্ত লিট্ল ম্যাগগুলির ‘কৃত্তিবাস’, ‘শতভিষা’ গোছের নাম বদলে যায়। আসে ‘ক্ষুধার্ত’, ‘জেব্রা’, ‘ফুঃ’-এর মতো কাগজ। সেখানে কবিতায় বাঁকাচোরা ইটালিক্স, মোটাদাগের বোল্ড ইত্যাদি হরেক রকমের টাইপোগ্রাফি ব্যবহৃত হত। পরবর্তী কালে সুবিমল মিশ্রের মতো অনেকেই নিজেকে হাংরি বলবেন না, বলবেন ‘শুধুই ছোট কাগজের লেখক’। কিন্তু তাঁদের গল্প, উপন্যাসেও আসবে সেই টাইপোগ্রাফিক বিভিন্নতা। তৈরি হবে শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন। হাংরিরা না এলে কি নব্বইয়ের দশকেও হানা দিতেন পুরন্দর ভাট?
আসলে, ম্যানিফেস্টোর মধ্যেই ছিল মৃত্যুঘণ্টা। ’৬২ সালে হাংরিদের প্রথম বাংলা ম্যানিফেস্টোর শেষ লাইন, ‘কবিতা সতীর মতো চরিত্রহীনা, প্রিয়তমার মতো যোনিহীনা ও ঈশ্বরীর মতো অনুষ্মেষিণী।’ হাংরিরা নিজেদের যত না সাহিত্যবিপ্লবী মনে করেছেন, তার চেয়েও বেশি যৌনবিপ্লবী।”
তিন
১৯১৭ সালে গিয়ম অ্যাপলিনেয়ার “সুররিয়ালিজম” অভিধাটি তৈরি করেছিলেন, যার অর্থ ছিল বাস্তবের অতীত। শব্দটি প্রায় লুফে নেন আঁদ্রে ব্রেতঁ, নতুন একটি আন্দোলন আরম্ভ করার পরিকল্পনা নিয়ে, যে আন্দোলনটি হবে পূর্ববর্তী ডাডাবাদী আন্দোলন থেকে ভিন্ন । ত্রিস্তঁ জারা উদ্ভাবিত ডাডা আন্দোলন থেকে সরে আসার কারণ হল ব্রেতঁ সহ্য করতে পারতেন না ত্রিস্তঁ জারাকে, কেননা কবি-শিল্পী মহলে প্রতিশীল্পের জনক হিসাবে ত্রিস্তঁ জারা খ্যাতি পাচ্ছিলেন। আঁদ্রে ব্রেতঁ সুররিয়ালিজম তত্বটির একমাত্র ব্যাখ্যাকারী হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে আরম্ভ করেন। ১৯১৯ সালে ত্রিস্তঁ জারাকে কিন্তু ব্রেতঁ চিঠি লিখে প্যারিসে আসতে বলেছিলেন । একইভাবে ‘হাংরি’ শব্দটি মলয় রায়চৌধুরী পেয়েছিলেন কবি জিওফ্রে চসার থেকে । এই ‘হাংরি’ শব্দটি নেয়ার জন্য মলয় রায়চৌধুরীকে যেভাবে আক্রমণ করা হয়েছে, তেমন কিছুই করা হয়নি আঁদ্রে ব্রেতঁ ও ত্রিস্তঁ জারা সম্পর্কে । মলয় রায়চৌধুরী হাংরি জেনারেশন আন্দোলন ঘোষণা করেন ১৯৬৫ সালের পয়লা নভেম্বর একটি লিফলেট প্রকাশের মাধ্যমে ।
পরাবাস্তববাদী আন্দোলনে, প্রথম থেকেই, আঁদ্রে ব্রেতঁ’র সঙ্গে অনেক পরাবাস্তববাদীর সদ্ভাব ছিল না, কিন্তু পরাবাস্তববাদ বিশ্লেষণের সময়ে আলোচকরা তাকে বিশেষ গুরুত্ব দেন না । আমরা যদি বাঙালি আলোচকদের কথা চিন্তা করি, তাহলে দেখব যে তাঁরা হাংরি জেনারেশন বা ক্ষুধার্ত আন্দোলন বিশ্লেষণ করার সময়ে হাংরি জেনারেশনের সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে অত্যধিক চিন্তিত, হাংরি আন্দোলনকারীদের সাহিত্য অবদান নিয়ে নয় । ব্যাপারটা বিস্ময়কর নয় । তার কারণ অধিকাংশ আলোচক হাংরি জেনারেশনের সদস্যদের বইপত্র সহজে সংগ্রহ করতে পারেন না এবং দ্বিতীয়ত সাংবাদিক-আলোচকদের কুৎসাবিলাসী প্রবণতা ।
আঁদ্রে ব্রেতঁ তাঁর বন্ধু পল এলুয়ার, বেনিয়ামিন পেরে, মান রে, জাক বারোঁ, রেনে ক্রেভালl, রোবের দেসনস, গিয়র্গে লিমবোর, রোজের ভিত্রাক, জোসেফ দেলতিল, লুই আরাগঁ ও ফিলিপে সুপোকে নিয়ে ১৯১৯ পরাবাস্তববাদ আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন । কিছুকাল পরে, রাজনৈতিক ভাবাদর্শের কারণে তাঁর সঙ্গে লুই আরাগঁর ঝগড়া বেধে গিয়েছিল । মার্সেল দ্যুশঁ, ত্রিস্তঁ জারা এবং আঁদ্রে ব্রেতঁ, উভয়ের সঙ্গেই ছিলেন, এবং দুটি দলই তাঁকে গুরুত্ব দিতেন, দ্যুশঁ’র অবাস্তব ও অচিন্ত্যনীয় ভাবনার দরুন।
পরাবাস্তব আন্দোলনের আগে জুরিখে ডাডাবাদী আন্দোলন আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল এবং আঁদ্রে ব্রেতঁ পরাবাস্তববাদের অনুপ্রেরণা পান ডাডা আন্দোলনের পুরোধা ত্রিস্তঁ জারার কাছ থেকে, কিন্তু ব্রেতঁ চিরকাল তা অস্বীকার করে্ছেন । ডাডা ছিল শিল্পবিরোধী আভাঁ গার্দ আন্দোলন ; অবশ্য প্রতিশিল্পও তো শিল্প । ডাডাবাদের রমরমার কারণে ত্রিস্তঁ জারার সঙ্গে ব্রেতঁর সম্পর্ক দূষিত হয়ে যায় ; একজন অন্যজনের নেতৃত্ব স্বীকার করতে চাইতেন না । ডাডা (/ˈdɑːdɑː/) বা ডাডাবাদ (দাদাবাদ নামেও পরিচিত) ছিল ২০ শতকের ইউরোপীয় ভিন্নচিন্তকদের একটি সাহিত্য-শিল্প আন্দোলন, যার প্রাথমিক কেন্দ্র ছিল সুইজারল্যান্ডের জুরিখে ক্যাবারে ভলতেয়ার ( ১৯১৬ নাগাদ ) এবং নিউ ইয়র্কে (প্রায় ১৯১৫ নাগাদ)। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় ডাডা আন্দোলন গড়ে ওঠে সেইসব শিল্পীদের নিয়ে, যাঁরা পুঁজিবাদী সমাজের যুক্তি, কারণ বা সৌন্দর্যের ধারণা মানতেন না, বরং তাঁদের কাজের মাধ্যমে প্রকাশ করতেন আপাত-অর্থহীন, উদ্ভট, অযৌক্তিক এবং বুর্জোয়া-বিরোধী প্রতিবাদী বক্তব্য । আন্দোলনটির শিল্পচর্চা প্রসারিত হয়েছিল দৃশ্যমান, সাহিত্য ও শব্দ মাধ্যমে, যেমন- কোলাজ, শব্দসঙ্গীত, কাট-আপ লেখা, এবং ভাস্কর্য। ডাডাবাদী শিল্পীরা হানাহানি, যুদ্ধ এবং জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে অসন্তোষ প্রকাশ করতেন এবং গোঁড়া বামপন্থীদের সাথে তাঁদের রাজনৈতিক যোগাযোগ ছিল।
যুদ্ধ-পূর্ববর্তী প্রগতিবাদীদের মধ্যেই ডাডার শিকড় লুকিয়ে ছিল। শিল্পের সংজ্ঞায় পড়েনা এমন সব সৃষ্টিকর্মকে চিহ্নিত করার জন্য ১৯১৩ সালে "প্রতি-শিল্প" শব্দটি চালু করেছিলেন মার্সেল দ্যুশঁ । কিউবিজম এবং কোলাজ ও বিমূর্ত শিল্পের অগ্রগতিই হয়তো ডাডা আন্দোলনকে বাস্তবতার গন্ডী থেকে বিচ্যুত হতে উদ্বুদ্ধ করে। আর শব্দ ও অর্থের প্রথানুগত সম্পর্ক প্রত্যাখ্যান করতে ডাডাকে প্রভাবিত করে ইতালীয় ভবিষ্যতবাদী এবং জার্মান এক্সপ্রেশনিস্টগণ । আলফ্রেড জ্যারির উবু রোই (১৮৯৬) এবং এরিক স্যাটির প্যারেড (১৯১৬-১৭) প্রভৃতি লেখাগুলোকে ডাডাবাদী রচনার আদিরূপ বলা যেতে পারে। ডাডা আন্দোলনের মূলনীতিগুলো প্রথম সংকলিত হয় ১৯১৬ সালে হুগো বলের ডাডা ম্যানিফেস্টোতে। এই ম্যানিফেস্টোর প্রভাবে পরবর্তিকালে ব্রেতঁ সুররিয়ালিস্ট ম্যানিফেস্টো লিখতে অনুপপ্রাণিত হন -- এই কথা শুনতে ব্রেতঁ’র ভালো লাগত না এবং সেকারণে তিনি বহু সঙ্গীকে এক-এক করে আন্দোলন থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন । তাছাড়া ব্রেতঁ মনে করতেন ডাডাবাদীরা নৈরাজ্যবাদী বা অ্যানার্কিস্ট, যখন কিনা তিনি একজন কমিউনিস্ট ।
ডাডা আন্দোলনে ছিল জনসমাবেশ, মিছিল ও সাহিত্য সাময়িকীর প্রকাশনা; বিভিন্ন মাধ্যমে শিল্প, রাজনীতি এবং সংস্কৃতি নিয়ে তুমুল আলোচনা হতো। আন্দোলনের প্রধান ব্যক্তিত্বরা ছিলেন হুগো বল, মার্সেল দ্যুশঁ, এমি হেনিংস, হানস আর্প, রাউল হাউসম্যান, হানা হৌক, জোহান বাডার, ত্রিস্তঁ জারা, ফ্রান্সিস পিকাবিয়া, রিচার্ড হিউলসেনব্যাক, জর্জ গ্রোস, জন হার্টফিল্ড, ম্যান রে, বিয়াট্রিস উড, কার্ট শ্যুইটার্স, হানস রিখটার এবং ম্যাক্স আর্নেস্ট। অন্যান্য আন্দোলন, শহরতলীর গান এসবের পাশাপাশি পরাবাস্তববাদ, নব্য বাস্তবতা, পপ শিল্প এবং ফ্লক্সেস প্রভৃতি গোষ্ঠীগুলোও ডাডা আন্দোলন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। এই আন্দোলনের অনেকে সুররিয়ালিস্ট আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন ।
পরাবাস্তববাদ আন্দোলনে যাঁরা ব্রেতঁর সঙ্গে একে-একে যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের অন্যতম হলেন ফিলিপে সুপো, লুই আরাগঁ, পল এলুয়ার, রেনে ক্রেভাল, মিশেল লেইরিস, বেনিয়ামিন পেরে, অন্তনাঁ আতো,জাক রিগো, রবের দেসনস, ম্যাক্স আর্নস্ত প্রমুখ । এঁদের অনেকে ডাডাবাদী আন্দোলন ত্যাগ করে পরাবাস্তববাদী আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯২৩ সালে যোগ দেন চিত্রকর আঁদ্রে মাসোঁ ও ইভস তাঙ্গুই । ১৯২১ সালে ভিয়েনায় গিয়ে ফ্রয়েডের সঙ্গে দেখা করেন ব্রেতঁ । ফ্রয়েডের ধারণাকে তিনি সাহিত্য ও ছবি আঁকায় নিয়ে আসতে চান । ফ্রয়েডের প্রভাবে ব্রেতঁ বললেন, সুররিয়ালিজমের মূলকথা হল অবচেতনমনের ক্রিয়াকলাপকে উদ্ভট ও আশ্চর্যকর সব রূপকল্প দ্বারা প্রকাশ করা। ডাডাবাদীরা যেখানে চেয়েছিলেন প্রচলিত সামাজিক মূল্যবোধকে নস্যাৎ করে মানুষকে এমন একটি নান্দনিক দৃষ্টির অধিকারী করতে যার মাধ্যমে সে ভেদ করতে পারবে ভণ্ডামি ও রীতিনীতির বেড়াজাল, পৌঁছাতে পারবে বস্তুর অন্তর্নিহিত সত্যে; সেখানে পরাবাস্তববাদ আরো একধাপ এগিয়ে বলল, প্রকৃত সত্য কেবলমাত্র অবচেতনেই বিরাজ করে। পরাবাস্তববাদী শিল্পীর লক্ষ্য হল তার কৌশলের মাধ্যমে সেই সত্যকে ব্যক্তি-অস্তিত্বের গভীর থেকে তুলে আনা।
সুররিয়ালিজমের প্রথম ইশতেহার প্রকাশ করেন ইয়ান গল। এ ইশতেহারটি ১৯২৪ সালের ১ অক্টোবর প্রকাশিত হয়। এর কিছুদিন পরেই ১৫ অক্টোবর আঁদ্রে ব্রেতঁ সুররিয়ালিজমের দ্বিতীয় ইশতেহারটি প্রকাশ করেন। তিনি ১৯৩০ সালে এ ধারার তৃতীয় ইশতেহারটিও প্রকাশ করেন। ইয়ান গল ও আঁদ্রে ব্রেতঁ—দুজনে দু দল সুররিয়ালিস্ট শিল্পীর নেতৃত্ব দিতেন। ইয়ান গলের নেতৃত্বে ছিলেন ফ্রান্সিস পিকাবিয়া, ত্রিস্তঁ জারা, মার্সেল আর্লেন্ড, জোসেফ ডেলটিল, পিয়েরে অ্যালবার্ট বিরোট প্রমুখ। আন্দ্রে ব্রেতঁর নেতৃত্বে ছিলেন লুই আরাগঁ, পল এলুয়ায়, রোবের ডেসনোস, জ্যাক বারোঁ, জর্জ ম্যালকিন প্রমুখ। এ দুটি দলেই ডাডাইজম আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ ছিলেন। অবশ্য ইয়ান গল ও আন্দ্রে ব্রেতঁ এই আন্দোলন নিয়ে প্রকাশ্য-রেশারেশিতে জড়িয়ে পড়েন। তখন থেকেই পরাবাস্তববাদীরা ছোটো-ছোটো গোষ্ঠীতে বিভাজিত হতে থাকেন, যদিও তাঁদের শিল্প ও সাহিত্যধারা ছিল একই । পরে আন্দোলনে যোগ দেন জোয়ান মিরো, রেমণ্ড কোয়েনু, ম্যাক্স মোরিজ, পিয়ের নাভিল, জাক আঁদ্রে বোইফার, গেয়র্গে মালকাইন প্রমুখ । জিয়োর্জিও দে চিরোকো এবং পাবলো পিকাসো অনেক সময়ে গোষ্ঠির কর্মকাণ্ডে অংশ নিতেন, তবে আন্দোলনের ঘোষিত সদস্য ছিলেন না।
সুররিয়ালিজম বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য ডাডাইজম থেকে নিলেও এই মতবাদটি, যে, ‘শিল্পের উৎস ও উপকরণ’ বিবেচনায় একটি অন্যটির চেয়ে স্বতন্ত্র্য। সুররিয়ালিজম আন্দোলনের সামনের সারিতে ছিলেন ফরাসি কবি আঁদ্রে ব্রেতঁ। তিনি শিল্প রচনায় ‘অচেতন মনের ওপর গুরুত্ব’ দেওয়ার জন্যে শিল্পীদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি মনে করতেন, ‘অচেতন মন হতে পারে কল্পনার অশেষ উৎস।’ তিনি অচেতন মনের ধারণাটি নিঃসন্দেহে সিগমুন্ড ফ্রয়েডের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। ডাডাবাদী শিল্পীরা শিল্পের উৎস ও উপকরণ আহরণে ‘অচেতন’ মনের ধারণা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না। সুররিয়ালিস্ট শিল্পীরা এসে অচেতন মনের উৎস থেকে শিল্প রচনার প্রতি গুরুত্ব দেন এবং সফলতাও লাভ করেন।
আঁদ্রে ব্রেতঁ মনে করতেন, ‘যা বিস্ময়কর, তা সবসময়ই সুন্দর’। অচেতন মনের গহীনেই বিস্ময়কর সুন্দরের বসবাস। তার সন্ধান করাই সাহিত্যিক-শিল্পীর যথার্থ কাজ। অচেতন মনের কারণেই সুররিয়ালিজমের কবি-শিল্পীরা গভীর আত্মঅনুসন্ধানে নামেন। মনের গহীন থেকে স্বপ্নময় দৃশ্যগুলো হাতড়ে বের করতে এবং মনের অন্তর্গত সত্য উন্মোচনে তাঁরা আগ্রহী ছিলেন। যার কারণে চেতন ও অচেতনের মধ্যে শিল্পীরা বন্ধন স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সুররিয়ালিস্ট শিল্পীরা অচেতন মনের সেই সব উপলব্ধিকে দৃশ্যে রূপ দিলেন যা পূর্বে কেউ কখনো করেনি। অচেতনের ভূমিতে দাঁড়িয়ে বাস্তব উপস্থাপনের কারণে খুব দ্রুতই এ মতবাদটি বিশ্ব শিল্পকলায় ‘অভিনবত্ব’ যোগ করতে সমর্থ হয়। এমনকী, পুঁজিবাদ-বিরোধী এই আন্দোলন থেকে উপকরণ সংগ্রহ করেছেন বহু বিখ্যাত বিজ্ঞাপন কোম্পানি ।
সুররিয়ালিজমকে ‘নির্দিষ্ট’ ছকে ফেলা কঠিন। সুররিয়ালিস্ট শিল্পীরা একই ছাতার নিচে বসবাস করে ছবি আঁকলেও এবং কবিতা লিখলেও, তাঁদের দৃষ্টি ও উপলব্ধির মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। ফলে এ মতবাদটি সম্পর্কে প্রত্যেকে ব্যাক্তিগত ভাবনা ভেবেছেন। ১৯২৯ সালে সালভাদর দালি এই আন্দোলনে যোগ দেন, যদিও তাঁর সঙ্গেও ব্রেতঁর বনিবনা হতো না । সালভাদর দালি মনে করতেন, ‘সুররিয়ালিজম একটি ধ্বংসাত্মক দর্শন এবং এটি কেবল তা-ই ধ্বংস করে যা দৃষ্টিকে সীমাবদ্ধ রাখে।’ অন্যদিকে জন লেলন বলেছেন, ‘সুররিয়ালিজম আমার কাছে বিশেষ প্রভাব নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। কেননা, আমি উপলব্ধি করেছিলাম আমার কল্পনা উন্মাদনা নয়। বরং সুররিয়ালিজমই আমার বাস্তবতা।’ ব্রেতোঁ বলতেন, ‘ভাবনার যথাযথ পদ্ধতি অনুধাবনের জন্যে সুররিয়ালিজম আবশ্যক।’ এ ধারায় স্বপ্ন ও বাস্তবতার মিশ্রণ হয় বলে সুররিয়ালিজমকে স্বপ্নবাস্তবতাও বলা হয়ে থাকে।
সুররিয়ালিজমের ঢেউ খুব অল্প সময়েই শিল্পের সবগুলো শাখায় আছড়ে পড়ে। কবিতা, গান থেকে শুরু করে নাটক, সিনেমা পর্যন্ত সুররিয়ালিস্টদের চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। ১৯২৪ সাল থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত সুররিয়ালিজম ধারায় অন্তত ছয়টি সিনেমা নির্মিত হয়। এ ধারার প্রধান শিল্পীরা হলেন জ্যাঁ আর্প, ম্যাক্স আর্নেস্ট, আঁদ্রে মেসন, সালভাদর দালি, রেনে ম্যাগরেট, পিয়েরো রয়, জোয়ান মিরো, পল ডেলভাক্স, ফ্রিদা কাহলো প্রমুখ। এ ধারার চিত্রকর্মের মধ্যে ১৯৩১ সালে আঁকা সালভাদর দালির ‘দ্য পারসিসটেন্স অব মেমোরি’ সবচেয়ে আলোচিত ছবি। এটি কেবল এ ধারার মধ্যেই আলোচিত চিত্রকর্মই নয়, এটি দালিরও অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিভার নিদর্শন। ‘দ্য পারসিসটেন্স অব মেমোরি’-তে দালি ‘সময়ের’ বিচিত্র অবস্থাকে ফ্রেমবন্দি করতে চেষ্টা করেছেন। ‘মেটামরফসিস অব নার্সিসাস’, ‘নভিলিটি অব টাইম’, ‘প্রোফাইল অব টাইম’ প্রভৃতি তাঁর গুরুত্বপূর্ণ কাজ।
সুররিয়ালিজম ধারার প্রধানতম চিত্রকর্মের মধ্যে রেনে ম্যাগরেটের ‘দ্য সন অব ম্যান’, ‘দিস ইজ নট এ পাইপ’, জর্জিও দি চিরিকো-এর ‘দ্য রেড টাওয়ার’, ম্যাক্স আর্নেস্টের ‘দি এলিফ্যান্ট সিলিবেস’, ইভ তঁগির ‘রিপ্লাই টু রেড’ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে সুররিয়ালিজম আন্দোলন থেমে যায়। শিল্পবোদ্ধারা মনে করেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষের মধ্য দিয়ে এ আন্দোলনটির অনানুষ্ঠানিক মৃত্যু ঘটে। কিন্তু অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আন্দোলনের মতো সুররিয়ালিজমের চর্চা বর্তমানেও হচ্ছে। বাংলাদেশের শিল্পাঙ্গনেও সুররিয়ালিজমের প্রভাব লক্ষ করা যায়। ১৯২৪ সালে প্রকাশ করেন তাঁর প্রথম সুররিয়ালিস্ট ম্যানিফেস্টো । মার্কসবাদের সঙ্গে আর্তুর র্যাঁবোর আত্মপরিবর্তনের ভাবনাকে একত্রিত করার উদ্দেশে ব্রেতঁ ১৯২৭ সালে ফরাসি কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন । কিন্তু সাম্যবাদীদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বেশিদিন টেকেনি । সেখান থেকেও তিনি ১৯৩৩ সালে বিতাড়িত হন । পরাবাস্তববাদীদের “উন্মাদ প্রেম” তত্বটি ব্রেতঁর এবং “উন্মাদ প্রেম” করার জন্য বেশ কিছু তরুণী সুররিয়ালিস্টদের প্রতি আকৃষ্ট হন । যৌনতার স্বেচ্ছাচারিতার ঢেউ ওঠে সাহিত্যিক ও শিল্পী মহলে ; পরাবাস্তববাদীদের নামের সঙ্গে একজন বা বেশি নারীর সম্পর্ক ঘটে এবং সেই নারীরা তাঁদের পুরুষ প্রেমিকদের নামেই খ্যাতি পেয়েছেন ।
তাঁর রাজনৈতিক টানাপোড়েন এবং অন্যান্য কারণে প্রেভের, বারোঁ, দেসনস, লেইরিস, লিমবোর, মাসোঁ, কোয়েন্যু, মোরিস, বোইফার সম্পর্কচ্ছদ করেন ব্রেতঁর সঙ্গে এবং গেয়র্গে বাতাইয়ের নেতৃত্বে পৃথক গোষ্ঠী তৈরি করেন । এই সময়েই, ১৯২৯ নাগাদ, ব্রেতঁর গোষ্ঠীতে যোগ দেন সালভাদর দালি, লুই বুনুয়েল, আলবের্তো জিয়াকোমেত্তি, রেনে শার এবং লি মিলার । ত্রিস্তঁ জারার সঙ্গে ঝগড়া মিটমাট করে নেন ব্রেতঁ । দ্বিতীয় সুররিয়ালিস্ট ইশতাহার প্রকাশের সময়ে তাতে সই করেছিলেন আরাগঁ, আর্নস্ট, বুনুয়েল, শার, ক্রেভাল, দালি, এলুয়ার, পেরে, টাঙ্গুই, জারা, ম্যাক্সিম আলেকজান্দ্রে, জো বনসকোয়েত, কামিলে গোয়েমানস, পল নুগ, ফ্রান্সিস পোঙ্গে, মার্কো রিসটিচ, জর্জ শাদুল, আঁদ্রে তিরিয়ঁ এবং আলবেয়ার ভালেনতিন । ফেদেরিকো গারথিয়া লোরকা বন্ধু ছিলেন সালভাদর দালি এবং লুই বুনুয়েলের, আলোচনায় অংশ নিতেন, কিন্তু সুররিয়ালিস্ট গোষ্ঠিতে যোগ দেননি । ১৯২৯ সালে তাঁর মনে হয়েছিল যে দালি আর বুনুয়েলের ফিল্ম “একটি আন্দালুসিয় কুকুর” তাঁকে আক্রমণ করার জন্যে তৈরি হয়েছিল ; সেই থেকে তিনি সুররিয়ালিস্টদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন । আরাগঁ ও জর্জ শাদুল ব্রেতঁ’র গোষ্ঠী ত্যাগ করেছিলেন রাজনৈতিক মতভেদের কারণে, যদিও ব্রেতঁ বলতেন যে তিনিই ওনাদের তাড়িয়েছেন ।
১৯৩০ সালে কয়েকজন পরাবাস্তববাদী আঁদ্রে ব্রেতঁ’র একচেটিয়া নেতৃত্বে বিরক্ত হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে একটি প্যামফ্লেট ছাপিয়েছিলেন । পরাবাস্তববাদ আন্দোলন দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় । ১৯৩৫ সালে ব্রেতঁ এবং সোভিয়েত লেখক ও সাংবাদিক ইলিয়া এরেনবার্গের মাঝে ঝগড়া এমন স্তরে গিয়ে পৌঁছোয় যে প্যারিসের রাস্তায় তাঁদের দুজনের হাতাহাতি আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল । এরেনবার্গ একটি পুস্তিকা ছাপিয়ে বলেছিলেন যে পরাবাস্তববাদীরা পায়ুকামী । এর ফলে পরাবাস্তববাদীদের ইনটারন্যাশানাল কংগ্রেস ফর দি ডেফেন্স অফ কালচার সংস্হা থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল । সালভাদর দালি বলেছিলেন যে পরাবাস্তববাদীদের মধ্যে প্রকৃত সাম্যবাদী হলেন একমাত্র রেনে ক্রেভাল । চটে গিয়ে ক্রেভালকে পরাবাস্তববাদী আন্দোলন থেকে বের করে দ্যান ব্রেতঁ । অঁতনা অতো, ভিত্রাক এবং সুপোকে পরাবাস্তববাদী দল থেকে বের করে দ্যান ব্রেতঁ, মূলত সাম্যবাদের প্রতি ব্রেতঁর আত্মসমর্পণের কারণে এই তিনজন বিরক্ত বোধ করেন ।
১৯৩৮ সালে ব্রেতঁ মেকসিকো যাবার সুযোগ পান এবং লিও ট্রটস্কির সঙ্গে দেখা করেন । তাঁর সঙ্গে ছিলেন দিয়েগো রিভেরা ও ফ্রিদা কালহো । ট্রটস্কি এবং ব্রেতঁ একটা যুক্ত ইশতাহার প্রকাশ করেছিলেন, “শিল্পের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা” শিরোনামে । লুই আরাগঁর সঙ্গেও ব্রেতঁর সম্পর্ক ভালো ছিল না । ১৯১৯ থেকে ১৯২৪ পর্যন্ত ডাডাবাদীদের সঙ্গে আন্দোলন করার পর ১৯২৪ সালে আরাগঁ যোগ দেন পরাবাস্তববাদী আন্দোলনে । অন্যান্য ফরাসী পরাবাস্তববাদীদের সঙ্গে তিনিও ফরাসি কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দ্যান এবং পার্টির পত্রিকায় কলাম ও রাজনৈতিক কবিতা লিখতেন । আরাগঁর সঙ্গে ব্রেতঁর বিবাদের কারণ হল ব্রেতঁ চেয়েছিলেন ট্রটস্কির সঙ্গী ভিকতর সার্জকে সন্মানিত করতে । পরবর্তীকালে, ১৯৫৬ নাগাদ, সোভিয়েত রাষ্ট্র সম্পর্কে নিরাশ হন আরাগঁ, বিশেষ করে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির বিংশ কংগ্রেসের পর যখন নিকিতা ক্রুশ্চভ আক্রমণ করেন জোসেফ স্তালিনের ব্যক্তিত্ববাদকে । তা সত্ত্বেও স্তালিনপন্হী আরাগঁ ও ট্রটস্কিপন্হী ব্রেতঁর কখনও মিটমাট হয়নি । কাট-আপ কবিতার জনক ব্রায়ন জিসিনকেও গোষ্ঠী থেকে বিতাড়ন করেন ব্রেতঁ ; ব্রায়ান জিসিনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ছিলেন বিট ঔপন্যাসিক উইলিয়াম বারোজ । বিট আন্দোলনের প্রায় সকলেই সুররিয়ালিজম দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন । বিটদের যৌন স্বাধীনতার ভাবনা-চিন্তায় সুররিয়ালিস্টদের অবদান আছে ।
পরাবাস্তববাদই সম্ভবত প্রথম কোনো গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন, যেখানে নারীকে দূরতম কোনো নক্ষত্রের আলোর মতো, প্রেরণা ও পরিত্রাণের মতো, কল্পনার দেবী প্রতিমার মতো পবিত্র এক অবস্থান দেওয়া হয়েছিল। নারী তাদের চোখে একই সঙ্গে পবিত্র কুমারী, দেবদূত আবার একই সঙ্গে মোহিনী জাদুকরী, ইন্দ্রিয় উদ্দীপক ও নিয়তির মতো অপ্রতিরোধ্য। ১৯২৯ সালে দ্বিতীয় সুররিয়ালিস্ট ম্যানিফেস্টোয় আদ্রেঁ ব্রেতঁ নারীকে এরকম একটি অপার্থিব অসীম স্বপ্নিল চোখে দেখা ও দেখানোর চেষ্টা করেছিলেন। পুরুষ শিল্পীদের প্রেরণা, উদ্দীপনা ও কল্পনার সুদীর্ঘ সাম্পান হয়ে এগিয়ে আসবেন নারীরা। হয়ে উঠবেন পুরুষদের আরাধ্য ‘মিউজ’ আর একই সঙ্গে femme fatale। সুদৃশ্য উঁচু পূজার বেদি উদ্ভাসিত করে যেখানে বসে থাকবেন নারীরা। তাঁদের স্বর্গীয় প্রাসাদে আরো সৃষ্টিশীল হয়ে উঠবে পুরুষ।
ব্রেতঁ ছিলেন সেই সময়ের কবিতার অন্যতম প্রধান পুরুষ। তাঁর সম্মোহক ব্যক্তিত্বে আচ্ছন্ন হননি তাঁর সান্নিধ্যে এসেও – এরকম কোনো দৃষ্টান্ত কোথাও নেই। উজ্জ্বল, সাবলীল, মেধাবী, স্বতঃস্ফূর্ত এবং নায়কসুলভ ব্রেতঁ একই সঙ্গে ছিলেন উদ্ধত, আক্রমণাত্মক ও অহমিকাপূর্ণ। নিজের তাত্ত্বিক অবস্থান থেকে মাঝেমধ্যেই ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে যেতেন। কিন্তু যদি তাঁর একবার মনে হতো যে কেউ তাঁর প্রভুত্বকে অগ্রাহ্য করছে, সর্বশক্তি দিয়ে তাকে আঘাত করতেন। নেতৃত্ব দেওয়ার সব গুণ প্রকৃতিগতভাবেই ছিল তাঁর মধ্যে। মহিলাদের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার ছিল তরুণ প্রেমিকের মতো সম্ভ্রমপূর্ণ। তাঁর আকর্ষণীয় বাচনভঙ্গি, অভিজাত ভাষা – এসবের সঙ্গে মাঝেমধ্যেই মেজাজ হারিয়ে সম্পূর্ণ লাগামহীন হয়ে পড়া আর দুর্বোধ্য জটিল মানসিকতার জন্য পারতপক্ষে অনেকেই ঘাঁটাতে চাইতেন না তাঁকে।
নারী পরাবাস্তববাদীদের সংখ্যা কম ছিল না । কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে উল্লেখ্য ফ্রিদা কাহলো, আসে বার্গ, লিজে দেহামে, আইরিন হামোয়ের, জয়েস মানসোর, ওলগা ওরোজকো, আলেহান্দ্রা পিৎসারনিক, ভ্যালেনটিন পেনরোজ, জিসেল প্রাসিনস, ব্লাঙ্কা ভারেলা, ইউনিকা জুর্ন প্রমুখ । নারী চিত্রকররা সংখ্যায় ছিলেন বেশি । তাঁদের মধ্যে উল্লেখ্য গেরট্রুড আবেরকমবি, মারিয়ন আদনামস, আইলিন ফরেসটার আগার, রাশেল বায়েস, ফ্যানি ব্রেনান, এমি ব্রিজওয়াটার, লেনোরা ক্যারিংটন, ইথেল কলকুহুন, লেনোর ফিনি, জেন গ্রাভেরোল, ভ্যালেনটিন য়োগো, ফ্রিদা খাহলো, রিটা কার্ন-লারসেন, গ্রেটা নুটসন ( ত্রিস্তঁ জারার স্ত্রী ), জাকেলিন লামবা ( আঁদ্রে ব্রেতঁ’র স্ত্রী), মারুহা মালো, মার্গারেট মডলিন, গ্রেস পেইলথর্প, অ্যালিস রাহোন, এডিথ রিমিঙটন, পেনিলোপি রোজমন্ট, কে সেজ ( ইভস তাঙ্গুইর স্ত্রী ), ইভা স্বাঙ্কমাজেরোভা, ডরোথি ট্যানিঙ ( ম্যাক্স আর্নস্টের স্ত্রী ), রেমেদিওস ভারো ( বেনিয়ামিন পেরের স্ত্রী ) প্রমুখ । ভাস্করদের মধ্যে উল্লেখ্য এলিজা ব্রেতঁ ( আঁদ্রে ব্রেতঁ’র তৃতীয় স্ত্রী ), মেরে ওপেনহাইম ( মান রে’র মডেল ছিলেন ) এবং মিমি পারেন্ট । ফোটোগ্রাফারদের মধ্যে উল্লেখ্য ছিলেন ক্লদ কাহুন, নুশ এলুয়ার, হেনরিয়েতা গ্রিনদাত, আইডা কার, দোরা মার ( পাবলো পিকাসোর সঙ্গে নয় বছর লিভ টুগেদার করেছিলেন ), এমিলা মেদকোভা, লি মিলার, কাতি হোরনা প্রমুখ । পুরুষ পরাবাস্তববাদীদের বহু ফোটো এই নারী ফোটোগ্রাফারদের কারণেই ইতিহাসে স্হান পেয়েছে ।
নারীদের নিয়ে পরাবাস্তববাদীদের এই স্বপ্নিল কাব্যময় উচ্ছ্বাস জোরালো একটা ধাক্কা খেল যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পশ্চিম ইউরোপে দ্রম্নত বদলাতে থাকা পরিস্থিতির ভস্ম ও শোণিত স্নাত শোণিত আত্মশক্তিসম্পন্ন নারীরা তাঁদের ভারী বাস্তবতা নিয়ে এসে দাঁড়ালেন সামনে। স্বপ্নে দেখা নারীর আয়না-শরীর ভেঙে পড়ল ঝুরঝুর করে আর বেরিয়ে এলো মেরুদ-সম্পন্ন রক্তমাংসের মানবী। সুররিয়ালিজম চেয়েছিল পুরুষের নিয়ন্ত্রণে নারীদের মুক্তি। কিন্তু যে গভীর অতলশায়ী মুক্তি দরজা খুলে দিলো নারীদের জন্য, সুররিয়ালিজম তার জন্য তৈরি ছিল না। মৃত অ্যালবাট্রসের মতো এই বিমূর্ত আদর্শায়িত ধারণা নারী শিল্পীদের গলায় ঝুলে থেকেছে, যাকে ঝেড়ে ফেলে নিজস্ব শিল্পসত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করা দুঃসাধ্য ছিল। সময় লেগেছে সাফল্য পেতে। কিন্তু দিনের শেষে হেসেছিলেন তাঁরাই। এমন নয় যে, পরাবাস্তবতার প্রধান মশালবাহক ব্রেতঁ চাইছিলেন যে পুরুষরাই হবেন এই আন্দোলনের ঋত্বিক আর দ্যুতিময় নারী শিল্পী এবং সাহিত্যিকদের কাজ হবে মুগ্ধ সাদা পালক ঘাসের ওপরে ফেলে যাওয়া এবং আকর্ষণীয় ‘গুজব’ হিসেবে সুখী থাকা। ১৯২৯ সালে দ্বিতীয় সুররিয়ালিস্ট ম্যানিফেস্টো প্রকাশের পরবর্তী প্রদর্শনীগুলোতে নারী শিল্পীরা সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন ঠিকই। কিন্তু পুরুষ উদ্ভাবিত পরাবাস্তবতা থেকে তাঁদের ভাষা, স্বর ও দৃষ্টিভঙ্গি ছিল স্বতন্ত্র। নিজেদের ভারী অসিত্মত্ব, শরীরী উপস্থিতি জোরালোভাবে জায়গা পেল তাঁদের ছবিতে।
কিন্তু নারী শিল্পীদের কাছে আত্মপ্রতিকৃতি হয়ে উঠল একটি সশস্ত্র ভাষার মতো। নিজস্ব গোপন একটি সন্ত্রাসের মতো। এই আন্দোলনের মধ্যে নারীরা এমন এক পৃথিবীর ঝলক দেখলেন, যেখানে আরোপিত বিধিনিষেধ না মেনে সৃজনশীল থাকা যায়, দমচাপা প্রতিবাদের ইচ্ছেগুলোর উৎস থেকে পাথরের বাঁধ সরিয়ে দেওয়া যায়। নগ্ন ও উদ্দাম করা যায় কল্পনাকে। নোঙর নামানো জাহাজের মতো অনড় ও ঠাসবুনট একটি উপস্থিতি হয়ে ছবিতে নিজের মুখ তাঁদের কাছে হয়ে উঠল অন্যতম প্রধান আইকন। যে ছবি আত্মপ্রতিকৃতি নয়, সেখানেও বারবার আসতে থাকল শিল্পীর শরীরী প্রতিমা। ফ্রিদা কাহ্লোর (১৯০৭-৫৪) ক্যানভাস তাঁর যন্ত্রণাবিদ্ধ শান্ত মুখশ্রী ধরে রাখল। মুখের বিশেষ কিছু চিহ্ন যা তাঁকে চেনায় – যেমন পাখির ডানার মতো ভুরু, আমন্ড আকারের চোখ ছবিতেও আনলেন তিনি। রিমেদিওস ভারোর (১৯০৮-৬৩) ছবিতে পানপাতার মতো মুখ, তীক্ষন নাক, দীর্ঘ মাথাভর্তি চুলের নারীর মধ্যে নির্ভুল চেনা গেল শিল্পীকে। আবার লিওনর ফিনির (১৯১৮-৯৬) আঁকা নারীরা তাদের বেড়ালের মতো কালো চোখ আর ইন্দ্রিয়াসক্ত মুখ নিয়ে হয়ে উঠল ফিনিরই চেনা মুখচ্ছবি। ১৯৩৯ সালের ‘The Alcove : An interior with three women’ ছবিতে ভারী পর্দা টাঙানো ঘরে দুজন অর্ধশায়িত মহিলা পরস্পরকে ছুঁয়ে আছেন। আর একজন মহিলা দাঁড়িয়ে। তিনজনেই যেন কোনো কিছুর প্রতীক্ষা করছেন চাপা উদ্বিগ্ন মুখে। যে তিনজন নারীর ছবি, তাঁরা যে লিওনর ফিনি, লিওনারা ক্যারিংটন এবং ইলিন অগার – এটা ছবিটিকে একঝলক দেখেই চেনা যায়। এমনকি যখন অন্য কোনো নারীর প্রতিকৃতি আঁকছেন তাঁরা, সেখানেও তাঁদের বিদ্রোহের অস্বীকারের জোরালো পাঞ্জার ছাপ এই শিল্পীরা সেইসব নারীর মুখে ঘন লাল নিম্নরেখা দিয়ে বুঝিয়ে দিতেন
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হতে ১৯৩৯ সালে অধিকাংশ পরাবাস্তববাদী বিদেশে পালিয়ে যান এবং তাঁদের মধ্যে আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও বক্তব্য নিয়ে খেয়োখেয়ি বেধে যায় । অলোচকরা মনে করেন যে গোষ্ঠী হিসাবে পরাবাস্তববাদ ১৯৪৭ সালে ভেঙে যায়, প্যারিসে “লে সুররিয়ালিজমে” প্রদর্শনীর পর । যুদ্ধের শেষে, প্যারিসে ব্রেতঁ ও মার্সেল দ্যুশঁ’র ফিরে আসার পর প্রদর্শনীর কর্তারা সম্বর্ধনা দিতে চাইছিলেন কিন্তু পুরোনো পরাবাস্তববাদীরা জানতে পারলেন যে একদল যুবক পরাবাস্তববাদীর আবির্ভাব হয়েছে, যাঁরা বেশ ভিন্ন পথ ধরে এগোতে চাইছেন । যুবকদের মধ্যে উল্লেখ্য ছিলেন ফ্রাঁসিস বেকঁ, আলান দাভি, এদুয়ার্দো পোলোৎসি, রিচার্ড হ্যামিলটন প্রমুখ ।
সুররিয়ালিজমের উদ্ভব সত্ত্বেও ডাডার প্রভাব কিন্তু ফুরিয়ে যায়নি, তা প্রতিটি দশকে কবর থেকে লাফিয়ে ওঠে, যেমন আর্পের বিমূর্ততা, শুইটারের নির্মাণ, পিকাবিয়ার টারগেট ও স্ট্রাইপ এবং দ্যুশঁ’র রেডিমেড বস্তু বিশ শতকের শিল্পীদের কাজে ও আন্দোলনে ছড়িয়ে পড়ছিল । স্টুয়ার্ট ডেভিসের বিমূর্ততা থেকে অ্যান্ডি ওয়ারহলের পপ আর্ট, জাসপার জনসের টারগেট ও ফ্ল্যাগ থেকে রবার্ট রাউশেনবার্গের কোলাঝে -- সমসাময়িক সাহিত্য ও শিল্পের যেদিকেই তাকানো হোক পাওয়া যাবে ডাডার প্রভাব, সুররিয়ালিজমের উপস্হিতি । ১৯৬৬ সালে মৃত্যুর আগে, ব্রেতঁ লিখেছিলেন, “ডাডা আন্দোলনের পর আমরা মৌলিক কিছু করিনি । ডাডা ও সুররিয়ালিজম আন্দোলনকারীদের ওপর প্রচুর চাপ সৃষ্টি করেছিল এবং কয়েকজন আত্মহত্যা করেন, যেমন জাক রিগো, রেনে ক্রেভেল, আরশাইল গোর্কি, অসকার দোমিংগেজ প্রমুখ । অত্যধিক মাদক সেবনে মৃত্যু হয় গিলবার্ত লেকঁতে ও অঁতনা আতোর ।
 মলয় রায়চৌধুরী | 27.58.255.50 | ১০ আগস্ট ২০২১ ১৯:৩০734848
মলয় রায়চৌধুরী | 27.58.255.50 | ১০ আগস্ট ২০২১ ১৯:৩০734848হাংরি আন্দোলন-এর অশ্লীলতা বিষয়ক ইশতাহার
[ ১৯৬৫ সালে ফালিকাগজের বুলেটিনে প্রকাশিত ]
আমি অশ্লীলতা সমর্থন করি ।
আমি ততদিন ওব্দি অশ্লীলতা সমর্থন করব, যতদিন ওইসব দুর্বৃত্ত অভিজাতরা তাদের পৈতৃক উৎকর্ষের নকল উৎসবের দাবি করতে থাকবে ।
আসলে অশ্লীলতা বলে কিছু নেই ।
অশ্লীলতা একটা নকল ধারণা, বানানো, উদ্ভাবিত,
তৈরি-করা,
নির্মিত
একদল অশিক্ষিত শ্রেণি-সচেতন ষড়যন্ত্রীর দ্বারা ; প্রতিষ্ঠানের অভিজাত শকুন দ্বারা, নিচুতলার থ্যাঁতলানো মানুষদের টাকাপুঁজ খেয়ে যারা গরম থাকে ; সেইসব মালকড়ি-মালিক জানোয়ারদের দ্বারা, যারা ঠাণ্ডা মাথায় এই নিচুতলার গরম হল্কার ওপরে একচোট মুরুব্বিগিরি করে ।
তাদের শ্রেণিগত সংস্কৃতি বাঁচাতে,
টাকাকড়ির সভ্যতাকে চালু রাখতে,
ঘৃণাভুতের পায়ে সৌরসংসারকে আছড়ে ফেলতে ।
সমাজের মালিকরা একটা নকল নুলো ভাষা তৈরি করে, নিচু শ্রেণির শব্দাবলীকে অস্বীকার করতে চায় যাতে বিভেদ রেখাটা পরিষ্কার থাকে ।
২
শব্দ আসলে শব্দ আসলে শব্দ আসলে শব্দ আর আমি অভিব্যক্তির কোনোরকম শ্রেণিবিভাগ হতে দেবো না । শুধুমাত্র এই অজুহাতে যে কোনো শব্দ, অভিব্যক্তি, গালাগালি, বাক্য বা উক্তি এক বিশেষ শ্রেণি/গোষ্ঠী/জাত/এলাকা/সম্প্রদায় কর্তৃক ব্যবহৃত, আমি কাউকে তা অস্বীকার, পরিত্যাগ, অগ্রাহ্য, প্রত্যাখ্যান করতে দেবো না ।
একটা শব্দ হলো ফাঁকা আধার যা ভরাট হবার জন্যে অপেক্ষমান ।
সেই সমাজ, যেখানে দুটো ভিন্ন আর্থিক শ্রেণির জন্যে দুরকম শব্দাবলী, তা অসুস্হ আর বিষাক্ত।
অশ্লীলতাকে প্রশ্রয় দেবো কেননা ভাষার মধ্যেকার শ্রেণিবিভাগ আমি নষ্ট ও ধ্বংস করে দেবো ।
তুমি যদি একজন অ্যাকাডেমিক মূর্খ হও এবং আমার কথায় তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না, তাহলে কলকাতার একজন রক্তপায়ী বাবুকে ধানবাদে নিয়ে গিয়ে সবচেয়ে পরিষ্কার খনিশ্রমিকের মাদুরে শুইয়ে দাও। সে তাকে মনে করবে অশ্লীল, ইতর, অসহ্য, এবং সমাজবিরোধী । সেই লোকটাকেই বম্বে বা প্যারিসে নিয়ে গিয়ে কোনো কেউকেটা রাজকুমার বা আলিখান বা বড়োসায়েবের পাশে শুইয়ে দাও ; সে তার শিরদাঁড়ার পায়ুবৃন্ত পর্যন্ত আহ্লাদে ডগমগ করে উঠবে :
ঘৃণা
অভিজাত মগজবাক্যে তরল ভ্যামপায়ার গড়ে তোলে কেননা ইশ্বরগোবর এই সফেদ কলারদের সর্বদা ভয়, এই বুঝি মানব সভ্যতাকে লোটবার তাদের অধিকার ও সুবিধা শেষ হয়ে গেল ।
অশ্লীলতা অভিজাতদের সংস্কার যারা নিচুতলার উন্নত সংস্কৃতির কৃষ্টি-আক্রমণকে ভয় পায় ।
৩
আসলে অশ্লীলতা হচ্ছে বুর্জোয়াদের বাড়িতে বানানো আত্মাপেষাই মেশিন ।
ঠিক যেমন তারা বানিয়েছে যুদ্ধ
গণহত্যা
বাধ্যতামূলক সৈন্যভর্তি
পুলিশের অত্যাচার কুঠরি
এবং আণবিক বোমা
নিজেদের লোকেদের ক্ষমতায় রাখতে
পৃথিবীর সমস্ত স্বর্ণপায়খানাকে তাদের পেটে ভরে নিতে
তাদের বিরোধীদের নিশ্চিহ্ণ করতে
মধ্যবিত্তের থুতুতে একদল সফেদকলার সৈন্য ডুবিয়ে রাখতে ।
আমি এদের চাই না
এই পোকাদের
আমি চাই পিটুইটারি আত্মাসুদ্দু মানুষ ।
একজন বুর্জোয়া সবসময় একজন ফ্যাসিস্ট বা একজন
কম্যুনিস্ট বা একজন প্রতিক্রিয়াশীল
কিন্তু কখনও মানুষ নয় ।
৪
অভিজাতের কাছে নিচুতলার ভাষা অশ্লীল । অভিজাতের কাছে তার নিজের ভাষা মানে শিল্প।
বুর্জোয়ারা মনে করে নিচুতলার ভাষা ব্যবহার করলে মানুষ এবং সমাজ ‘কলুষিত ও বিকৃত’ হয়, কেন না তারা ভালো করেই জানে যে, এই ধরণের বুজরুকি ছাড়া তাদের সমাজ-সংস্কৃতি বেশিদিন টিকবে না।
এই ষড়যন্ত্র এক্কেবারে কাণ্ডজ্ঞানহীন ।
সমগ্র সমাজের সাধারণ ভাষায় কথা বলা এবং লেখা যদি কলুষিত ও বিকৃত করা হয়,
তাহলে আমি মানুষকে কলুষিত ও বিকৃত করে প্রকৃতিস্হ করব ।
মানুষের তাবৎ শব্দাবলী যতক্ষণ না গ্রহণযোগ্য হয়, আমি অশ্লীলতা সমর্থন করব । আমি চাই কবিতাকে জীবনে ফিরিয়ে দেয়া হোক ।
আমি ইচ্ছে করে তেমন লেখা লিখবো, যাকে বুর্জোয়ারা অশ্লীল মনে করে, কেন না আমি তাদের হিঁচড়ে নিয়ে গিয়ে বাধ্য করব তাদের ওই নকল উৎকর্ষের বিভেদ ভেঙে ফেলতে । আর এর জন্যে কলকাতার কম্যুনিস্ট বুর্জোয়া, প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া এবং ফ্যাসিস্ট বুর্জোয়া আমার বিরুদ্ধে একজোট হয়ে আমায় তাদের জেলখানায় ঢুকিয়ে দিলেও কিছু এসে যায় না ।
মানুষ ও মানুষের মধ্যে পার্থিব দখলিসত্তের ভিত্তিতে কোনো তফাত করতে দেবো না ।
পৈতৃক রুপোর চামচে করে সমাজের একটা অংশ কিছু শব্দকে খায় বলে, আমি তাদের উন্নত মনে করি না ।
৫
যে সমাজে পার্থিব দখলিসত্তের ভিত্তিতে মানুষে-মানুষে তফাত, সেখানে যৌনতা পুঁজি হিসেবে ব্যবহৃত।
সেক্স পুঁজিরুপে ব্যবহৃত ।
বুর্জোয়া-অত্যাচারিত সমাজ একটা বেবুশ্যেঘর,
কিন্তু কেন যৌনতা পুঁজি হিসেবে ব্যবহৃত ?
কেননা পৃথিবীতে যৌনতাই একমাত্র ব্যাপার যাতে ক্ষুদ্রতা নেই
সংস্কৃতির
ঐতিহ্যের
ধর্মের, জাতির
ঐশ্বর্যের
দেশের, প্রথার, সংস্কারের এবং আইনের ।
অবচেতনার টুঁটি চেপে ধরার জন্যেই যৌনতাকে পুঁজি করা হয় ।
যৌনমাংসের তেল-তেল গন্ধ ছাড়া এই সমাজে কোনো বিজ্ঞাপন সফল নয় এবং কোও কাজই টকটকে যোনির ফাঁদ না পেতে করিয়ে নেয়া সম্ভব নয় । প্রতিটি পদক্ষেপে অবশ্যম্ভাবী যৌনজাল কেননা এই সমাজ-ব্যবস্হা ক্রেতা-বিক্রেতার তৈরি ।
মানুষ এবং/অথবা মানুষী এই সংস্কৃতিতে হয়ে ওঠে প্রতীক বা বস্তু, অর্থাৎ জীবন বদলে যায় ‘জিনিস’-জড়পদার্থে ।
যৌনজীবন যদি হয়ে ওঠে সহজ সরল স্বাভাবিক, তাহলে এই সিঁড়ি-বিভাজিত সংস্কৃতি ধ্বসে পড়বে, আর ওই সুবিধা-লোটার-দল তাদের ফাঁপা অন্তর্জগতের মুখোমুখি হয়ে পড়বে ।
তাই জন্যে যৌনতার র্যাশনিং
তাইজন্যে ধীরেসুস্হে যৌনবিষের ফেনা
তাইজন্যে পরিপূর্ণ যৌন-উপলব্ধি বারণ
তাইজন্যে যৌনতাকে স্বাভাবিক করতে দেয়া হবে না,
তাই জন্যে পুঁজি ছাড়া অন্য কোনো রকমভাবে যৌনতাকে প্রয়োগ করতে দেয়া হয় না : কবিতায় তো কখনই নয় : কেননা কবিতার সঙ্গে কিছুই প্রতিযোগিতা করতে পারে না ।
শৈশব থেকেই সমাজের প্রতিটি ও তাবৎ মস্তিষ্ককে ভুল শিক্ষায় ভ্রষ্ট করা হয়, এবং এই নষ্টামিকে বলা হয় নৈতিকতা । শাসনকারী বুর্জোয়া সম্্রদায় জানে যে যতদিন এই অসুখকে নীতিজ্ঞান বলে চালানো যায়, আর যে কোনোভাবে মধ্যবিত্তের ভেতরে এটা ছড়িয়ে দেয়া যায়, তাদের কর্তৃত্ব বহাল থাকবে ।
৬
উচ্চবিত্ত টাকা-খুনিরা সাহিত্যে যৌনতার অন্য প্রয়োগ অশ্লীল ঘোষণা করবে, কেন না আইনগত ও সামাজিক উপায়ে তারা জঘন্য হিংস্রতায় নিজের শত্রুদের নিশ্চিহ্ণ করবে যাতে যৌনতাকে পুঁজি ছাড়া অন্য উপায়ে ব্যবহার করা না হয় ।
বুর্জোয়ারা যাকে অশ্লীল বলে, আমি ইচ্ছে করে তাইই লিখবো, যাতে যৌনতাকে পুঁজি হিসেবে ব্যবহারের ব্যাপারটা ধ্বংস ও ছারখার করে দিতে পারি ।
যৌনতা মানবিক ;
মেধাশক্তিই অনাক্রম্য ; যা অনাক্রম্য তা নীতিজ্ঞান ।
আমি যৌনতাকে ‘জিনিস’ হিসেবে প্রয়োগ করতে দেবো না । সেনসর পদ্ধতি সেই ভয় থেকে জন্মায় যাকে নীৎশে বলেছেন ‘যূথের নীতিজ্ঞান’ ।
বুর্জোয়াদের দাবি যে, কোনো বই বা কবিতা পড়ে মানুষ ও সমাজ ‘কলুষিত এবং বিকৃত’ হয়ে উঠবে কারণ তাতে যৌনতাকে স্বাভাবিকতা দেয়া হয়েছে ।
৭
আমি, মলয় রায়চৌধুরী, জন্ম ১১ কার্তিক
আমি অশ্লীলতা সমর্থন করি,
আমি জানি, কলকাতার বুর্জোয়া দুর্বৃত্তরা
আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ছকে ফেলেছে,
আমার তাতে কিছু যায় আসে না ।
এই সভ্যতার পতন কেউ থামাতে পারবে না
আমি ভবিষ্যৎবাণী করছি ।
আমার যেমন ইচ্ছে আমি সেরকমভাবে লিখবো, এবং সমগ্র বাঙালি মানবসমাজের শব্দভাঁড়ারে নিজেকে চুবিয়ে দেবো।
আমার সমস্ত শরীর যা ভাবে, আমি সেটাই ভাববো
আর যারা জানতে চায় তাদের জানাবো
কিংবা কাউকে
যে এই কথাগুলো জানার জন্যে জন্মাবে ।
আমি কবিতাকে জীবনে ফিরিয়ে দিতে চাই ।
জীবনে যা-কিছু আছে তার সমস্তই থাকবে কবিতার অস্ত্রাগারে ।
 মলয় রায়চৌধুরী | 27.58.255.50 | ১০ আগস্ট ২০২১ ১৯:৩২734849
মলয় রায়চৌধুরী | 27.58.255.50 | ১০ আগস্ট ২০২১ ১৯:৩২734849আমার নও : পোস্টমডার্ন গল্প
মলয় রায়চৌধুরী
আজ্ঞে, এঁরা সব পেচক সম্প্রদায়ের। ছুটি শুরু হয়ে গেছে। আশা করি ভোর সাড়ে দশটার মধ্যে কাঁটাশয্যা থেকে গাত্রোৎপাটন করবেন। ফেলাশিও থেকে নাকি প্যাপিলোমা ভাইরাস আসে? তা হোক তা হোক কতকিছু থেকেই তো আসে যায় কর্কট রোগ তবু সেই শিবনেত্র তবু সেই সিলিঙের ফ্যানেদের অলস গানের মৃদু গ্রীষ্মে ধীরে ধীরে পেকে ওঠা এ ফল প্রাণের হাতের মুঠোয় ধরা বীজের তরল তার পরে শিল্পিত উঠে যাওয়া যায় সঙ্কোচন প্রসারণ অলক্ষ্য তাই মুখ টিপে হেসে চলে যাই ধীরে ধীরে সোজা হওয়া পায়ের পাতায় ফেলাশিও থেকে নাকি হতে পারে কর্কট রোগ? সমুদ্র বলে ওঠে, তা হোক তা হোক হে কাগা, রে কাগা, কাআগা রে! কাঃ কাঃ কাঃ আহ আহ আহ ঘর অন্ধকার, তার স্বাদ পর্দা ধুন্দুল, আর বাইরে দেয় গুল কত রান্না কত কথা কত সংসারের দারুণ প্রমাদ শুধু তুই আজ বাইরের দূত চাস যদি ঢুকে আয়, ইতস্ততঃ খা আর গা হে কাগা এ কাগা, কাগা রে! কাঃ কাঃ কাঃ আহ আহ আহ এ শব্দ কিসের শব্দ? কালোনুনিয়া দেখতে কেমন ? খুবকালো? মাঝারিকালো? নাকি দুলকিআলো ? খেতে খেমন ? দেখলেই খিদে পায় ? নাকি যখন তখন ? ঘ্রাণ ? গন্ধ আছে কোনো? নাকি আঠালো ফুলের আঠার মতন ? শক্ত খুব? নাকি নরম ? নাকি মুখে দিলেই গ'লে যায় এমন ? ডগাটা নরম ! কালোনুনিয়া দেখতে কেমন ? রডের মতন নাকি ঝলসানো রডোড্রেনড্রন ? চোরার ঘরে চোরা , তেইলা চোরা, যায়গায় খায় যায়গায় ব্রেক, কাইত হইয়া খায় চিত হইয়া মরে, লাফাইয়া খায় দাফাইয়া মরে। ময়নার মার ঘুম নাই,হাসিনার মার খাতা নাই। ইঁদুর-চিকার মারামারি নষ্ট করে বাসাবাড়ি, ঔষধ লাগান তাড়াতাড়ি। ধরা পড়লে জামিন নাই, ইঁদুর কইবে আয়রে ভাই দেশ ছাইড়া বিদেশ যাই! একদাম ২০ টাকা ২০ টাকা ২০ টাকা ।
জংধরা রেলপথে যেন কোন রেলগাড়ি অশ্বত্থের ঘেরাটোপ বটের ক্যানোপি মাকড় কলোনি ছিঁড়ে চলার মতন আগে পাশে হাতড়ায় কোন তাড়াতাড়ি নেই কোন তাড়াতাড়ি রেলগাড়ি! খোলো মুখ, রাখো হাত, উহ কি মিঠে অসুখ ওফ কাগা বোস। আআ হাহাহা হে কাগা ও কাগা কাগা রে ম্যাগির খিচুড়ি । লিরিকাল করে বানানো। কোনো কথা হবে না। যেমন স্বাদ, তেমন গন্ধ ! কোনো চিনাকে খাওয়ালে মাও জে ডঙ ভুলে বাড়ি থেকে নড়বে না, গোলাম হয়ে থাকবে। সাধে বলে জাতে গোরিলা ; অন্তরমহল সন্ধ্যে হয়ে আসছে। লাল আর কালচে আকাশ ।ঝাঁকে ঝাঁকে ফিরে যাচ্ছে পাখিরা ।'বাসায়' । নিজস্ব বাসা ।মানব ঘাটে বসে থাকে ।সময় কাটে ।কাটেওনা ।জলের ভেতর ঘাই মারে মাছ ।দূরে ,বহূ দূরে একটা শিল্যুট । ক্রমশ আবছা থেকে স্পষ্ট হয় । বিকেলে ঝঞ্ঝাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে আড্ডাগলির চুল্লু উৎসবে মুগ্ধতা ছড়িয়ে দিলেন মঞ্জুলাদি। আমরা আপ্লুত।ধন্যবাদ…..
আমার গুরুদেবদাদুভাই বলতেন, প্রকৃত কীর্তনশিল্পী হচ্ছেন সেই মাধ্যম যিনি ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক গড়ে দেন। তাঁদের উদ্দ্যেশে প্রণাম রেখো। যে চরম ভাবাবস্তায় দূর দূর বিচরণ করে আত্মা, সঙ্গীত ছাড়া সে ভাব আর কিসে? স্বর্গ নেমে আসে সুরের কাছে এখানেই। একটা নৌকো ।মাঝির বয়স হাজার বছর তিন মাস । ঘাটে এসে লাগে নৌকো । কোঁচকানো চামড়ার ভেতর কোটরাগত চো়খ । ঘন সাদা চুল,সাদা দাড়ির ফাঁকে সাদা দাঁত ।নিকষ প্রেতের মত লাগে । মাঝি ওকে চেনে । দুমাস হলো মানুষটা এসেছে এখানে । রোজ এভাবেই বসে থাকে । এদিকটা গ্রাম থেকে দূরে ।সচরাচর আসেনা কেউ ।ভাঙাচোরা ঘাট,আগাছা আর ভুতের উপদ্রব ।দূরে ধ্বংসস্তুপ দানব অট্টালিকা ।দু ধাপ নীচে বসে মাঝি । সুলেমান । একটা বিড়ি ধরায় । মানবকে একটা দেয় । চুপ চাপ ।রাত বাতাস খেলা করে দুজনের মাঝে । কি যেন বলতে চায় মাঝি । প্রিয় ঠোঁট- প্যাস্টেল। প্রিয় আকুতি- পরকীয়া। প্রিয় বৃক্ষ- বিবাহ। প্রিয় আকাশ-আরন্যক। প্রিয় ধ্বনি- হরিণী। প্রিয় রাগ- অনন্তনাগ। প্রিয় নক্ষত্র-শরৎ। প্রিয় স্পর্শ- রসাতল। প্রিয় আলাপন- শিহরণ। প্রিয় শব্দ–নৈঃশব্দ। প্রিয় আলেখ্য-চম্পক। প্রিয় মানুষ-মৃগয়া। তাবৎ শক্তিমত্তা আর পবিত্রতা সমেত মৃত এই রাষ্ট্র ঈশ্বরের ..."ভিনসারেমো", তাবৎ শক্তিমত্তা আর পবিত্রতা সমেত এই রাষ্ট্র বলে উঠলেন--খুনের জন্য দায়ী এই ছুরি তৈরির কৌশল গোলাপ আর বৃষ্টির ঘ্রাণে মুগ্ধ ছিল সন্ধ্যার দখিনা বায়, রাত্রি নেমেছে চোখের কাজলের গভীরে, ক্লান্তিগুলো ঢেকে রেখেছি ।
ঢেউ- চোখ। প্রিয় পলক- দারুচিনি। শেষ বিকালবেলা ঘুমোলে যুবতীদের মেজাজ খুব খিটমিট খিটমিট ! কখন কোথায় কি মুখ ফসকে যায় - নিজেরে বলেই চলে…..ব্যাস সবাই মিলে মতামত দেওয়া শুরু হয়ে গেছে। লাভ হবে কি? হয়েছে এর আগে? তখনও তো মতামত দিয়েছিলেন। মতামত না দিয়ে বরঞ্চ জনমত তৈরী করুণ। পারবেন? যে লোকে বাঙালি খাবার খেতে রেস্তরাঁয় যায়, তা বাড়িতেও তো জমিয়ে রান্না করা যায়। কী সুন্দর সব মাছ মাংসের পদ, নারকেল দুধ দিয়ে শুক্তো, ছানার কোপ্তা, সোনা মুগ ডাল, বাহারি চাটনি.... সে সব ছেড়ে গুচ্ছ কাঁড়ি টাকা খসিয়ে রেস্তরাঁয় কেন বাপু! এসব তো আমাদের ঘরের সম্পদ, তাকেও বাণিজ্যিক করে তুলব? আর এসব যদি এই বেলা শিখে না নিই আমাদের ছেলেমেয়েরা তো রান্না করতেই জানবে না। হারিয়ে যাবে নারকেল নাড়ু, মুড়িঘন্ট, ইলিশ ভাপা। তালের বড়া দোকান থেকে কিনে খাই, ছানার ডালনা হয়ে গিয়েছে পনির, নটে শাকের করলা ঘণ্ট খেতে গেলে শ্যামবাজারের পাইস হোটেল । বাঙালি ঘরের রান্নার গন্ধ, কড়াইয়ে খুন্তির ঠুংঠাং সেকি নাচ নয়? উৎসব মানে কি শুধু হেয়ার স্পা, প্যান্ডেল হপিং আর রেস্তরাঁয় বসে খাবারের থালা সাজিয়ে ছবি? সব শেষে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি, "ওহ, কী লাকচে!" বলে কেউ যদি রাস্তায় চেঁচায়- ওইখানেই থাবড়িয়ে দাঁত ভেঙে দেওয়া হবে। ধন্যবাদ...
প্রিয় রিমঝিম-সোনাঝুরি প্রিয় সাঁতার-অপেক্ষা। প্রিয় জ্যোতিষ্ক- নীরবতা। প্রিয় চুম্বন-রেবতী। প্রিয় স্মৃতি-বাঁশরী। প্রিয় বিস্ফোরণ-কুঞ্জবন। প্রিয় রঙ-শ্রীরাধিকা। বেঁচে থাকা? সে এক ধ্রুপদী মলাট মৃত্যু? সে তো পরম প্রচ্ছদ এটিকে কি পরকীয়া বলা যায় আমি জানতে চাইছি....আমার লেখা শেষ চিঠি, আর লিখবো না, কখনো না, আর কোনোদিন কিছু জিগ্যেস করবো না। তুমি তোমার বউয়ের জন্য ৩৫০০ টাকার দামি শাড়ি কিনে এনেছো, সেই শাড়িটা আমিই পছন্দ করে কিনে দিয়েছি। অথচ আমার জন্য একমুঠো দোপাটি ফুল আনতেও তোমার হাত কেঁপেছে .... তোমায় ভাবতে হয়েছে, আসা যাওয়ার পথে কেউ দেখলো কিনা, তোমায় পেছনে ফিরে ঘুরে দেখতে হয়েছে বারবার। মাথার চুল ট্যু পায়ের নখ ইস্ত্রিমার্কা সাজগোজ করে ছিঁচকে দুঃখ সাজাবেন? মিনিমাম একটি আলোমিছিল? এসব দেখে আমারই চুদে দিতে ইচ্ছে করে, বিশ্বাস করুন। মাভৈঃ বলে নগ্ন হয়ে রাজপথে নামুন এক হয়ে। দিকে দিকে। পিতা নয়, পিতৃব্য নয়, ভাই - বন্ধু নয়, স্বামী নয়, পুরুষ, তুই দেখ! দেখ! পারবেন তো মা, পারবে তো বোন? সময় আর নেই যে -- এখুনি --মাতলা'য় ছিল রাতজাগা চুপ তোমার অধরা সহিষ্ণুতায় বাধুক ঈশ্বরীর হরবোলা খুশি,কাঞ্চনমালা তুমি অনুরাগ মুছে চর্চিত রাগে রাজবেশে গেলে অন্তঃপুরে আমার একলা বসনে বিলাপ তুমি শুনেছিলে রাত পারাবারে...
এরপরে কিছু গোপন থাকেনি লোকালয়ে বাঁচা গরাদ জীবনে মানে খুঁজে খুঁজে অরণ্য বাঁচে আমি বাঁচি কারো ছেঁড়া অভিধানে । বুকে ভালোবাসা নিয়ে বেড়ে ওঠা মানুষগুলো ঠকতে জন্মায় ;বাঁচতে না...বেঁচে থাকার একটা নেশা আছে! ধমনীর লাল রক্ত যেন সুরা, উষ্ণধারা শাখা-প্রশাখায় বইছে। ছোট ছোট আশা-আকাঙ্খা যেন পালতোলা নৌকো; ঘাট হতে ঘাটে ভেসে চলেছে। ঠিক সময়ে একজন আসবে, কিছুদিনের জন্য সবকিছু ভুলিয়ে দিতে… ঘিজতাঘিজাঙ নেশার ওপর নেশা চড়াতে, লাল-নীল-সবুজ স্বপ্নের চাঁদোয়া টাঙাতে। পেছন দিকের দরজা খুলে যাবে; নির্জন দাওয়া। তিন ধাপ সিঁড়ি, ঘাসে ঢাকা পথ, ছোট্ট জলাশয়, কাচের মতো টলটলে জল, অদ্ভুত বাতাস।
চুল-চোখ-নাক-কন্ঠস্বর, স্পর্শ সব একেবারে আলাদা। ভীষণ এক ভালোলাগা! আসলে এসব কিছুই নেই, কল্পনা। এ কল্পনা কেন এলো? কেমন একটা ভিজে ভিজে ভাব, 'মনটারে তুই ভাগা রে কাগা' এ হলো পাগলামি। কে সে? মাথার ওপর দিয়ে একটা পাখি উড়ে গেছে। ডানার বাতাস! কোন ডালে বসলো - এ কী বলা যায়! তবু, আর একবার যদি দেখা হয়! এসব সময়ে বেশি কিছু বলতে ইচ্ছে হয়না, এটুকুই বলতে চাই, সব্বাইকে ভালোবাসা সম্ভব নয়, কিন্তু মানুষ মানুষকে সম্মান করুক, তার প্রাপ্য সম্মানটুকু দিক, মানুষ আর একটা মানুষের ইমোশনের কদর করুক...বহু জায়গায় দেখেছি দুটো মানুষ আমন্ত্রিত, কিন্তু গুরুত্ব একটা মানুষকে বেশি দেওয়া হয়, আর একজনকে কম। আপনি জানেন না হয়তো সেই সময় ওই মানুষটার কতটা খারাপ লাগতে পারে।হয় নেমন্তন্ন করবেন না নইলে সম্মান করবেন।একটু চোদা খাওয়ার জন্য আমি কত কিছু করি,,,,,, ইচ্ছে করে ছোট ভাই কে দিয়ে করিয়ে নিই আমার ভোদায়,,,,,,,, ভাই যখন শুয়ে থাকে আমি গিয়ে ওরটা নাড়তে থাকি,, এইতো কাজ হয়ে গেল, আমায় বাগানের ঘাসে, আমার ভোদাটা একটু বিদেশি...মেরেলিন মনরোইস্ট, কোমরের তলায় বালিশ... ওহহ কীইযে শান্তি...টি এস এলিয়ট বলে গেছেন।
ঘরের লোক মেলায় গেলে, আমায় ঘরে ডেকে আমার শরীরের উপর উঠে বসতে কিন্তু একবারও তোমার পা কাঁপেনি.... তোমার বউ স্মার্ট, নাক টিকালো, লাল টিপ পরে, গায়ের রং ফর্সা, তাই তুমি সেকেন্ডে সেকেন্ডে ফোন করে খোঁজ নাও, সে শাড়ির সাথে কোন ব্লাউজটা ম্যাচিং করে পরলো, হাই হিলস পরলো, নাকি ফ্ল্যাট....কোন শেডের লিপস্টিক মাখলো ঠোঁটে, অফিসে থাকতে থাকতে তুমি তাকে ছবি পাঠাতে বলো কয়েক ঘন্টা অন্তর অন্তর, তাকে কেমন দেখতে লাগছে জানতে চাও! আহা আজ বৃষ্টি হয়েছে, রাস্তায় জল জমা, সে কিভাবে যাবে তার বাপের বাড়ি, এই চিন্তায় তুমি কম্পিউটারের সামনে বসে ভুল টাইপ করে গেছো দিনের পর দিন!....সে বিরক্ত হয়ে গেলেও তুমি রেয়াত করো নি! অথচ আমায় একটা ফোন করার সময় দরজায় ছিটকিনি লাগাতে হয়েছে তোমায়, চাদর মুড়ি দিয়ে ফিসফিস করে কথা বলতে হয়েছে। একবার বলেছিলাম একটা চিঠি লিখতে, তুমি ব্যঙ্গ করে সেকেলে বলে হেসেই উড়িয়ে দিলে....
কবে একটা ডানডিয়া নাইটের নিমন্ত্রণ করল একজন। কী ভয়ের ব্যাপার। কলকাতা যাব রে। লোকজন আমাকে নাক উঁচু বললে তাই। ভাই রক্ষা কর আমায় । এসবে আমি নেই। সন্ত্রাসীরা কোপাচ্ছিল স্বামীকে। আর সেই খুনিদের দুই হাতে জাপটে ধরে স্বামীকে বাঁচাতে চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন স্ত্রী। চিৎকার করে অন্যদের সাহায্য চাইছিলেন। কিন্তু কোনো কিছুতেই কাজ হয়নি। শেষ পর্যন্ত স্বামীকে বাঁচাতে পারেননি মিন্নি। বরগুনার মাইঠা এলাকার নিজ বাড়িতে বসে স্বামী হত্যার সেই ভয়াল স্মৃতির বর্ণনা দেন মিন্নি। একটি ভীষণ মন খারাপের ছবি।জাহ্নবী ধরে রয়েছে মোম মায়ের হাত।শোক বড় ব্যক্তিগত। তারাই বোঝে যারা হারিয়েছে ছাতা।প্রোটেকশন দিতে পারিনি। গানপয়েন্টের মুখ। মেলে দিয়েছি গতর। সাম্প্রতিককালে এমন রঙিন রানওভার দেখেছ কি ? বুককেস থেকে সরাসরি সম্প্রচারিত ব্যাকলেস ব্রা। এমন মৃদু ফ্লেভার হ্যালোজেন শুঁকেছ? দ্যাখো। চাখো। আসহোল। আয়োডিনের ঝাঁঝ নাও। তারপর ... তারপর ...মাদার-সিস্টার থেকে সেরে ওঠো হে অ-যৌনসিস্টেম...
কথাবার্তা না, দল থেকে তাড়িয়ে দেয়া না।চোঁ-চোঁ দৌড় না, পাকড়ে ফেলা না।ছোটা একেবারেই নিষেধ।ধুমপান নিষেধ। চোদা বারণ। হাত্যারের আজ কুড়িতে পা। চারিদিকে এত চাকচিক্কের মধ্যে কোথাও গিয়ে ভুলে থাকা সত্যিগুলোকে সাধারণ এর সামনে বিবস্ত্র করার অঙ্গীকারটুকু নিয়ে আমাদের এগিয়ে চলা। হাতে হাত রেখে একসাথে আরোও বড় হব আমরা। হ্যাঁ হাম লড়েঙ্গে সাথি, উদাস মওসাম কে খিলাফ। হাম লড়েঙ্গে তবতক, যবতক লড়নে কি জরুরত বাকি হোগি...শালা হিন্দি ছাড়া বলতে পারিস না বাঞ্চোৎ। তুমি তোমার প্রিয় মানুষটার জন্য গা ভর্তি গয়না এনে দাও, প্রতিটা গয়না আমার পছন্দ করা! আমি তখন বাথরুমে, আমার চোখ বেয়ে নেমেছে গর্ভজল। তুমি তো জানো মেয়েদের কাছে গয়নার গুরুত্ব ততটাই যতটা বাঁধানো ফ্রেমের কাছে ছবির কিংবা মুষড়ে আসা স্মৃতির কাছে ফেলে যাওয়া পায়ের ছাপের....কিন্তু জানো তো প্রাণঘাতী বোমার আওয়াজও বড় সুমধুর লাগে তোমার বউএর গা ভর্তি গয়নার আওয়াজের চেয়ে...আমি তোমারটা কখনো ছুঁতে চাইনি, তোমার সাথে কিছু মুহূর্ত একটা পাহাড়ঘেঁষা ছোট্ট কাঠের বাড়িতে কাটাতে চেয়েছিলাম, এই ধরো একদিনের সংসার...ঘিজতাঘিজাঙ ঘিজতাঘিজাঙ সারারাত....
' আমার না জন্মানো মেয়ের নাম মারুঙবুরু '.....ফিরে আসাটা বা ছেড়ে আসা ,তার মাঝখানে একশীর্ণ লাল সিগন্যালে দাঁড়িয়েছিল ,সেই রাস্তাটার নাম লাতিন কোয়ার্টার। এই শহরটা এমনিই। সঠিক আলোর খোঁজেই তো পথে নামা। অথচ বাহকের হাতে মরণ বন্ধক রেখে সাড়ে সাত মাইল আকাশই দেখলাম একনাগাড়ে। তার আগে দাঁড়িয়েছিলাম ঝর্ণার রেলিং ঘেঁষে। সবুজ থেকে আরও সবুজতর হয়ে দেখেছি বাতাসের সঙ্গে বাতাস কথা বলছে, " প্রফুল্ল,চিনতে পেরেছ ?"এই তির্যকটার প্রয়োজন ছিল। একটা পোর্সেলিনের ফুলদানি কেঁপে উঠেছিল কারণ হাওয়া বদলের সংশয় থেকে সেও মুক্ত নয়। ধরা পড়া'র পরের অধ্যায়ে কোনও অজুহাতই ধোপে টেকেনি। চাঁদ একটা আরামকেদারের মতই আধখানা হয়ে ঝুলছে। মাঝে মাঝে একটু কাত করে ঢেলে দিচ্ছিল ম্যাগমা। নক্ষত্রবেষ্টনী ছেড়ে কতটুকুই বা এগোনো যায় ! বা পৌঁছানো। মাইনাস ডিগ্রিতে একটা সম্পর্ক মরুদ্যানের গল্প বলছে। শুনতে পাচ্ছি , কিন্তু দেখতে পাচ্ছি কম।সম্পর্ক আর দূরত্বের অনুমান নির্ভুল বলি কী করে। মাইনাস পাওয়ারের চশমাটা মাঝে মাঝে ইচ্ছাকৃতভাবে প্লাস পাওয়ার হয়ে যায়...
কাকুদ্বয়, বিস্তারিত চাই। আমার যখন তখন বহুকিছু ক্ষিদে পায়। মুক্তির দিনে বন্ধনের প্রকট হাতছানি ... মানতে হয় নাহলে... নোটে গাছটি মুড়িয়ে গল্পের শেষ দাঁড়ি টানতে হয় ...." প্রথমাবধি ঐশীবোধের লালন ছিল শ্রী বিশ্বনাথের অন্তরে। এ প্রসঙ্গে তাঁর আধ্যাত্মিকবোধ সম্পর্কে দু একটা কথা না বললেই নয়। তথাকথিত গ্রিকদেবীর মোহময়ী পৌত্তলিকতা নয়, তাঁর আধ্যাত্মিক বোধ ছিল সমন্বয়বাদী অসাম্প্রদায়িক উদার মানবতাবোধ। তিনি পরম্পরায় বিশ্বাসী ছিলেন এসরাজবাদক। যে কোনো বিশেষণই কম পড়ে কিছু মুগ্ধতা কে প্রকাশ করতে গেলে। ফ্যাশন ঘুরেফিরে আসে। কিশোরীবেলার আমব্রেলা কাট এবার জোরদার ফ্যাশন। ১৯২০-তে জন্মানো মা বলত এটা তার বালিকাবেলার কাট। কিনেছি এবার দুটো ছাতা, চিনের তৈরি বলে সস্তার তিন অবস্হা...কিন্তু মাওয়ের দেশ।
বিষাদ ধারণে সে অনন্তগর্ভিণী এখন নিরাপদে পেরোয় যাবতীয় সম্ভাব্য অলীকের মৃত রন্ধ্রগুলি । এই ধরায় একা উনি অন্ধকারকে 'নিস্তেল' পেয়েছেন , এমন কি ? দীর্ঘকাল পর পরিত্যক্ত অশ্বথখচিত ছাদে দাঁড়ালে নিজেকে জাতিস্মর ভ্রম আসে বহু জনেরই । ছাদে অশ্বথ্থ দেখলেই বিলডার গোঁত্তা মারবে । যার কুণ্ডলীতে বিষযোগ থাকে , একা সেই প্রেমিকা উন্মাদিনী । কখনো কেউ ভাবে বিসর্জনের দুর্ভাগ্য লেখা হয় একমাত্র উপলক্ষেরই বিধিতে ? জলস্তর বাড়লে কী পার্থক্য গো-ক্ষুর আর সমুদ্রে ? সীমানার ক্ষত নিয়ে কত সহস্র হত্যা রোজ সসাগরা পৃথ্বীতে । ধান খেয়ে যায় মোহবাসবেরা , দ্বন্দ্ব প্রচুর , কূর্ম না নোয়া , কে ভেসেছিলো আগে ? যার গরলবর্ষা তুমি নিতে পারোনি , পরিযায়ী উড়াল তোমারই দিগন্তে সে কেন ভাসাবে ? করুণার রং উগ্র পাণ্ডুর অথবা পিত্ত প্রবণ, নিবিড় সমঝোতা থাকায় স্বাভাবিক প্রতিবর্তে কখন যে পরম শূণ্য ছুঁয়েছে ,জানা যায়নি । অনুকম্পা। করুণা। এই সব কারো কাম্য হতে পারে? যদি হয় তাহলে কিছু বলার নেই কিন্তু যদি না হয় তাহলে জানতে চাইবো কেউ কেউ নিজের বুকে ছুরি দিয়ে এই দুটো অনুভূতির পাওয়ার আশা লেখে কেন?
বড় হচ্ছিনা একটুও ;এতটাই বড় হয়ে যেয়ো না যে তুমি ভুলে যাবে মাঠ।সেই তুমি পায়ের আঙুলে খেলা করতে পাথর নিয়ে,কিছুক্ষন বাদে সোজা শট।চু কিৎকিৎ, ভোকাট্টা বা খেলার শেষে চুরমুরে লাগানো আঙ্গুল চেটে নেওয়ারস্বাদ ভুলে যদি যাও জানো তুমি করবে পাপ। হ্যাঁ সেই রকমই দুস্টুমি নিয়ে যখন গুলতি ছুড়তে, বা কাঁচের গুলি নিয়ে ছোট বেলার সব ইকড়ি মিকড়ি বন্ধুগুলো হাফ পেনটুল ,ধুলো মাখা ফ্রকে গোল্লা ছুট......ছুটতে ছুটতে গো স্ট্যাচু রেডি,চোর পুলিশেরধপ্পা বা রুমাল চুরি লজেন্সের ভাগে ভাব ,আচারে আড়ি। রেনল্ডস বা রোটম্যাক পেন এখনো বড্ড দরকারী। কাবাডির জিত বিশেষত ঘাসের মাঝে, কাদা মেখে শুষে নিতে ঘ্রাণ বৃষ্টির ।এতটাই বড় হয়ে যেয়ো না যে তুমি ভুলে যাবে পরবের শেষে নিমকিনাড়ু বা খিচুড়ির প্লেটে একসাথে পাঁচজন কাড়াকাড়ি। শীতের দুপুরে কমলার কোয়ার ভাগ বা উল কাঁটায় মা কাকিমার বোনা ঘর গুলো জুড়ে গিয়ে তোমার স্কুলের সোয়েটারে স্নেহ ঝরে পড়তো পশমের আদরে। এতটাই বড় হয়ে যেয়ো না যে তুমি ভুলে যাবে তোমার ভিতর একটা শৈশব আছে। এখনো অনেক ভিড়ের মাঝে তাকে খুঁজো। ঠোঁটের কোণে তখন হাসির ঘিজতাঘিজাঙ ফিরে পাবে...
সমর্থনের মাধুকরি যাচ্ঞা করেছো দ্বারে ও দ্বিপ্রহরে । অমানিশার মধু অপার্থিবই থেকেছে সেমত নিঃস্ব এ হিরণ্ময় ঘোরে । সমর্পণ প্রার্থিত থাকে প্রথম অর্ধের পতঙ্গসূত্র মাত্রেই , বলো কয়টি কণ্ঠ, মন্থনের ধারক হতে পারে ? অবশেষে এক আশ্চর্য ছায়াসম্ভব আলো আমায় নিষ্কৃতি দেয় , যতো ছিল অমায়াপ্রসূত ভালোবাসা সমুদয় , প্রাচীন ও প্রাণ্তিক প্লাটফর্মের মতো ক্রমে ভ্রম মনে হয় । কিছু শ্রাবণে ধারা বড় বিহ্বল রেখেছিলো জাগতিক রূপগাথা আর অনিবার্য বিপর্যয়ের কারনামায় । আদ্রর্তাহীন মাদকতা অভ্যাসে ফিরিয়েছে প্রতি ধ্যানান্তে বৃক্ষতলটি ভোলার । ঠাকুর বাড়ির ছাদে মাতঙ্গিনী গঙ্গোপাধ্যায় মানে কাদম্বরী দেবীর আত্মহত্যার ১৩৫ বছর পরেও সেই ছাদে এখনো প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে….আত্মহত্যাকারিণীরা অমর হয়।
তুমি দেখো অকালমৃত্যু , আমি জানি বিচ্ছেদের আতঙ্ক কতদূর তীব্র হলে প্রেমিকের করতলে হত্যারেখা জাগ্রত হয় । এক যোগীর কথা পড়েছিলাম,এক বৃক্ষতলে দুইবার ধ্যানে বসতেন না,পাছে মায়া পড়ে যায়। মেঘ আর বিদ্যুতের রহস্য ভেদে যে আলো দ্বিতীয় গ্রহে আসে,তার তাপ ফুটন্ত বাষ্পের সামান্য দ্বিরাগমনে বাপের বাড়ী আসা মেয়েটির সখী সান্নিধ্যের আতঙ্কের থিম লিভটুগেদার সদ্য-বিধবার থেকে আলাদা নয়।অশুভ মহাদেশকে আবিষ্কারের ব্যর্থতা যে কোনোদিন লোনাজল খায়নি তাকে বোঝানোর সমতুল্য।আসলে কী জানো আমি কোনোদিন যাইনি তোমার কাছে যে গিয়েছিল তা একটি শরীর দুটি বুক থার্টি সিক্স বি একটি যোনি আর তাকে ঘিরে কয়েকটি লোমকূপ আর একটি গর্ত আশ্চর্য ব্যাপার দ্যাখো তোমার ওই কেঁচো আমার এই গর্তকে গিলেও ফেলতে পারলো না….
সম্ভ্রান্ত গণিকালয়ে মান রক্ষার্থে যে পুরুষ বাস্তুকে বাজি রাখে,ব্যাসদেবের বাইরে তার পরিণতি চাইছি- "ড্রাকারিস"। ক্ষমা এমন এক অবস্থান উন্মাদ নগ্নিকা, দানের কাপড়ে ঠিক যে দৃষ্টি দেয়। যে হাঁস, ঝাঁক থেকে আলাদা হয়ে কসাই পুকুরে পৌঁছে যায় পরম বিশ্বাসে,তার মাংস বাজারে আলাদা করে বিক্রি হয় না।হত্যাকারী সন্তানকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার পর মহিলা বিচারকটি নিব না ভেঙে তুলে রাখেন গর্ভপাতের স্মারক হিসাবে। কর্মসূত্রে আসা যাওয়ার পথে 'বেইমান-দেউড়ি' পড়ে। আকাশকে ব্যথা শোনানোর রাত পেরিয়ে প্রতি সকালে দেখি ক্ষয়িষ্ণু রক্তরঙের ইঁটের খাঁজে খাঁজে অজস্র মলিন বিশ্বাসঘাতকতা। পাঁজরে তীব্র দংশন ধবল কোন শ্বেতাম্বরী পেঁচা আসেনা।একাহারী শরীরের চোষক,সফল এক বাদুড় আত্মা থেকে উড়ে গিয়ে মিলিয়ে যায় বিপুল আলোর উৎসবে।সিসে রঙের হাওয়ায় কান পাতলে প্রতিধ্বনি আসে শেষ স্বাধীনতায় কোন যুদ্ধ হয়নি।পরিকল্পিত ছিলো প্রতারণা। প্রিয় বান্ধবীর নাভিতে 'ভালো' দস্তখত পড়ে এসেফাই এর আটকানোর কথাও না কারণ ভোটগুলো তো বিজেপিতেই দিয়েছে। বাম যে রাম হয়েছে সেটা বোঝাই যায়৷ আর সবাই যদি ওই আটকানোর বিপক্ষেই থাকে তাহলে পরের দিনের ওই র্যালিটা কি শুধু ইউএসডিএফ আর র্যাডিকাল মিলে করেছে? ইউএসডিএফ বা র্যাডিকাল যদি আটকে থাকে তবে বেশ করেছে৷
সিরাজদের কোন ঈশ্বর থাকেনা। ক্ষমতার খেলা চলে ব্যভিচারি আলেয়ায়।নেশাগ্রস্তের বমনে উঠে আসে সবুজ সন্দেহ,ঘৃণিত কৌশলের অপাচ্য মাধুকরিকে দাঁড় বেয়ে আনবে বর্ষা? মায়েরা জানে না কীভাবে একই গর্ভ থেকে প্রসব হয় সন্ত ও হত্যাকারী। প্রেমিকের কষ্টে টাকরায় আওয়াজ তুলি সান্ত্বনার বা আফশোসের নয়, আরামের। পাথরভরা বুক, যেমন বলেছিলেন গালিব এই নিষ্ঠুর বুক আমার সম্পদ। নয়তো এত ভালোবেসেছি জীবনে টুকরো টুকরো হয়ে কবেই ধুলো হয়ে যেতাম "দুশমনি জম কর করো,পর ইতনি গুঞ্জায়েশ রহে,কি ফির কভি হাম দোস্ত বন যায়ে তো শরমিন্দা না হো"। আবার শালা হিন্দি ফিলমের ঘিজতাঘিজাঙ । রাজা গণেশের কিছু পরে বঙ্গের দুই প্রসিদ্ধ কবি আবির্ভূত হন। চন্ডীদাস ও কৃত্তিবাস। আদি বাঙালি কবি এঁরাই। কিন্তু শিক্ষা বিষয়ে সাধারণ বাঙালি সমাজ অনেক পেছনে তখন থেকেই। মিথিলা তখন সংস্কৃতচর্চ্চার বাজার। আর সে যুগের লেখাপড়া মানেই হল সংস্কৃত । নদীয়াবাসী কৃত্তিবাসকেও ‘পাঠের নিমিত্ত গেলাম বড় গঙ্গাপার’ মানে বরেন্দ্রভূমিতে যেতে হয়েছিল। রেখে যাওয়া বলতে তো সে এক আধখাওয়া নদীজল মুগ্ধতার জরুরী বৈঠক তাকে আমি বরং করে তুলি।
রেখে যাওয়া বলতে তো মন্দির দালানের কোলে মিহি আতাগাছ যার ছুঁয়ে শুরু হয়েছিল অজস্র রূপকথার তোতাসংবাদ। শশ্যদানা খুঁটে নিচ্ছে মৃদু চারণায় পাখিসব করে রব শেষ বাস চলে যাচ্ছে তুমি ছায়া হাত নাড়ছো হাওয়া জানালায়। বাইরেটা ফিরতে চাইছে প্রবেশের অনুনয় নিয়ে আর শিখে নেওয়া গ্লাসনস্ত নরম করে উঁকি দিচ্ছে ডানাভাঙার ইতিহাস অনুপুঙখ একটি নিটোল গল্প সন্ধ্যার ফিসফিস মেখে ক্রমশ প্রবিষ্ট। অপরাহ্ন এইসব সময়ের কুচি অম্লান হাতভরে স্লোগান হয়ে ক্রমউচ্চারণ নৈ:শব্দের তীব্র বোধনে। কুয়াশার রং চিনে চিনে বড় হয়ে উঠছে বিজন আঙিনায় হাসি গান ব্যাথা যত কথা সংবলিত ঘিজতাঘিজাঙ। উপযুক্ত চাকরির মতোই এই পশ্চিমবঙ্গে উপযুক্ত ছেলেমেয়েদেরও অভাব দেখা দিয়েছে বোধহয়।তাই ঠাকুর পো ও বৌদিদের ডিমান্ড বেড়ে চলেছে মার্কেটে শঙ্খচূড় বনবেহাগী মল্লারী কানহা তানবাদন বাঁশুরি রিক্ত শ্বাস ঔদাসীন্য কর্ণকুহরে পঙ্গু বাদুর ঝালর অশনি অমাবস্যায় পাতালগর্ভে কুমিরাশ্রু হা করা বিচিত্র গুহায় চন্দ্রাহত মধ্যযাম ভ্রূয়ের কাকতালীয় মধ্যাহ্ন উড়োচুলে ধুম ঘন্টাকাল নিথর মৈথুনী ভাতঘুম কচি খাদ।
দুটি জীবন আছে।এক, জলের ওপর যেমন সাঁতার , ভেসে ।এ হল লড়াই।বাঁচতে গেলে ভেসে থাকতেই হবে যে।দ্বিতীয়টি হল ডুবসাঁতার।এ হল সাধনা।এখানে ডুবে যাওয়ার ভয় নেই। ডুবে থাকাই আনন্দ ; সংসারে ভেসেই থাকো। আর একটা জীবন হলো সাধনা। গৃহকর্তার মাইনেতে সুরে তাল মিলিয়ে চলা! না হলে স্কটল্যান্ড থেকে ফিরে ১১ ঘন্টার বিমান যাত্রার গা ব্যথা সারতে না সারতে আবার ভ্রমণ এবং হোটেলে চোদা !সত্যি বলছি বেড়াতে সবারই ভালো লাগে,কার নয়? কিন্তু এক স্যুটকেসের জিনিস নামিয়ে গোছাতে না গোছাতে আবার তাড়া...কন্ডোম না থাকলে হ্যাঙ্গামের একশেষ ! বলতে গেলে শেষ হবেনা।আমাদের সেদিনই সকালে সাহারা মরুভূমি যাবার কথা, সেখান থেকে মরোক্কো। কাঁইগুঁই করে যাওয়াটা ভেস্তে দিলাম।
কচলে সুগন্ধি লেবু মণিকোটরে আগুনক্ষিধে জাত তিক্ততার বৈরাগ্য জিহ্বায় সন্ন্যাস।নাভিতলে পাংশুটে মাধুকরী খোয়াই তলিয়ে অন্ধধীবর মণিদর্পনের চিবুকে রক্তিম অনশ্বর চাঁদ নিভু জ্যোৎস্না আঁচে সেঁকে সান্ধ্য-প্রেমিকের প্রসারিত চাতালের ভৌগলিক চিত্র...ইজেলের যোনিকেশে ক্লান্তি ঘামতেলে নৈপুণ্য শীৎকার ঊরুসন্ধি খাওয়াই বিন্দুবিসর্গ কালসাপের আড়িমাড়ি ঠেস চাপাকলে মাড়াই রুয়ি বন্ধ্যাজমিনে সাওয়ান-ভাদে বীজধানে পুংগতি। আড়ষ্ট দধিমঙ্গলে ডুব পানকৌড়ির শিরচ্ছত্র এলোকেশীর ঊরুজঙ্ঘায় জাহ্নবীর হুমড়ি স্রোত কামমর্দন। চুপকথায় দুঃশাসন দ্রৌপদীকাল রজঃস্বলার ক্ষীর আঁচলের উন্মোচন স্নিগ্ধ পুরুষদুগ্ধ বক্ষটোপরে অবৈধ স্তনবৃন্তে হামাগুড়ি। যোনিওষ্ঠে মদ্যপ ঝঞ্ঝা আলতা পায়ে প্রশ্রয় একরাশ রতিক্লান্তি।মই হামানদিস্তায় সেচ গেরস্থালীর চৌকো সাপলুডো…
গোগ্রাসে থলথলে মাটির চৌম্বকীয় সূচের অনভিপ্রেত আবেশ। জীবনের পথটা নেহাৎ ছোট নয়, এই অ-ছোট পথ পাড়ি দিতে গেলে পরিচয় হয় অনেকের সাথেই, কারো কারো সাথে গড়ে উঠে সম্পর্ক। সম্পর্ক গড়া সহজ কিন্তু রক্ষা করা পকেটের মাশুল , অ-যোগাযোগে সম্পর্কেও ছাতকুড়া(ছত্রাক) পড়ে। তার উপ্রে আবার এখন যোগ হইছে ভার্চুয়াল সম্পর্ক, আসল সম্পর্ক যেখানে রাস্তায় গড়াগড়ি খায়,সেখানে ভার্চুয়াল সম্পর্ক আর কতক্ষণ, কতদিন? কারো কারো কাছে ভাইয়া, দাদা,দাদান,দিদি, বুবু,আপুন, বুবুন ডাকগুলো হয়তো কেবল বাচনভঙ্গির মাধুর্য বাড়ায়, কিন্তু কারো কারো কাছে এই সম্বোধনগুলো হাড় মাংস ভেদ করে হৃৎপিণ্ড ছুঁয়ে যায়। অনুবাদ কে পড়ে? পড়েই কী আদৌ! প্রায়ই হতাশায় ভেঙে পড়ি। কেন অনুবাদ করি! লাভ কী এভাবে প্র্যাকটিক্যালি ঘুম বিশ্রাম বেড়ানো রিল্যাক্স করা সব বাদ দিয়ে অনুবাদ করার! কে তাড়া দিয়েছে এমন? ফাঁক পেলেই অপমান করতে চায় কত বাজারি লেখক সম্পাদক। তবু জেদ। তবু দাঁতে দাঁত চেপে লড়া।
আমি একেবারেই একরোখা মানুষ, কেউ তালি বাজানোর জন্য হাত যদি কিঞ্চিৎও না বাড়ায় তবে আমি আর হাত বাড়িয়ে বেশিক্ষণ রাখতে পারি না, হাত ব্যথা করে। তথাপি আমি মানুষ ভালবাসি, মনের মত বন্ধু হলে জানকুরবান! মানুষের উপকার করতেই ভাল্লাগে। তবে কোন সম্পর্কই একতরফা হয় না। বিশদ আলোচনায় ধৈর্য নাই। ভালকথা আমি ইকটু তিতা কথা বলি তাই আমার সাথে কারো সম্পর্ক হয় না, বাট যদি কারো সাথে হয় তো মর্ছি, খুব বৃষ্টি হলে আগে রোমান্টিক হয়ে যেতাম। আম্মা মারা যাবার পর খুব বৃষ্টি হলো। কবর টা ভেঙ্গেচুরে একাকার। আমি উন্মাদের মত চিৎকার করতে থাকলাম। আমার মনে হচ্ছিলো এই যে ভাঙ্গা জায়গা দিয়ে পানি যাচ্ছে, আমার মা ডুবে যাচ্ছে! যতো ভুলে যেতে চাই, বৃষ্টি আমাকে তার চাইতেও বেশি ঝরিয়ে দেয়। সারাজীবন দিয়েই যাবে। উৎসবে বৃষ্টি হবে না, চাপ নিস না।-----হ্যাট তুই আবহাওয়াবিদ কবে থেকে হলি রে?-----আমি বলছি তো হবেনা, সব ব্যাপারেই তোর পাকামি! -----হু হু বাওয়া! শালা তুই আমার মন বুঝিস না, জলবায়ু কি করে বুঝলি বে!... ----ফর ইওর কাইন্ড ইনফরমেশন ম্যাডাম ওটা জলবায়ু নয়, আবহাওয়া হবে। জলবায়ু আর আবহাওয়ার মধ্যে বিস্তর পার্থক্য আছে, ছোটবেলায় পড়াশুনায় কাঁচা ছিলি জানি, তা বলে সেটা লোক জানানোর কি দরকার...-----ওই হলো! আমি আবহাওয়াই বলেছি, বেশি পাকা! কথায় কথায় ভুল ধরবি না...------অবশ্যই ধরবো, আর তোর ভুলটাই ধরবো অন্য কারোর টা না। যাতে অন্য কেউ না ধরতে পারে তোর ভুল, তোকে কেউ অপমান না করতে পারে! তোকে সবথেকে বেশি অপমানটা আমিই করবো আবার সমস্ত আদরটাও আমিই করবো, আর কেউ না....-----এমনিতে আদর তো করতে পারিস না, আবার বড় বড় কথা, হুর....------ফোনের মধ্যে আদর আমার দ্বারা হবে না, সামনে আয়, কাছে আয়, হয়তো তোকে দেখলে জড়িয়ে নেবো গায়ে, কেঁদেও নেবো খানিক। জানিস যখন একলা থাকি, এক-এক সময়ে ইচ্ছে করেই তোকে ফোন করি না। তুই ভাবিস অন্য কারোর সাথে ব্যস্ত আছি....রাগে তো তোর মুখ ফুলে যায়, কিন্তু আমি তোকে নিয়ে ব্যস্ত থাকি, তোকে একদম নিজের মতো করে পেতে চাই। মনে হয় তুই আমার সামনে বসে আছিস, অনবরত বকে যাচ্ছিস। আমি যত বলছি চুপ কর চুপ কর, তুই কোনো কথাই শুনছিস না।
বেশি হাঁটলে আমার পায়ে ফোস্কা পড়ে।-----তো আমি কি করবো! কোলে নিয়ে হাঁটবো নাকি! ----সে তো জানি, তোর ক্ষমতা নেই!----ব্যাপারটা ক্ষমতার নয়, আমি আদরটা ঘরের ভেতরে করাই পছন্দ করি, যেখানে তোর আমার মধ্যে একটা মাছিও না ঘ্যানঘ্যান করতে পারে। শুধু তোর শ্বাসের আওয়াজ আর বুকের স্পন্দনটুকু ছাড়া আমাদের মধ্যে আর কিচ্ছু আসবে না।আমাদের গরম নিঃশ্বাস টুকু একে অপরের কাঁধে গিয়ে পড়বে, আমাদের বুকের ভেতর জমানো বরফ ধীরে ধীরে গলে যাবে, যেভাবে মোমবাতি গলে দেশলাইএর কাছে এলে....----অনেক রাত হলো, আমরা কি ঘুমাবো না আজ?---- অপেক্ষা করছি, ঘুমো...·খুব খুব খারাপ লাগে এই একবিংশ শতাব্দীতেও যখন এই ধরনের ঘটনা চোখে পড়ে। খুব খাঁটি কথা । সত্যি একটা মানুষের যোগ্যতার বিচার তার বাহ্যিক সৌন্দর্য্য কেন হবে? কেন একটি মেয়েকে সারাজীবন তার গায়ের রঙের জন্যে আত্মীয়, পাড়াপ্রতিবেশিদের থেকে কটু কথা শুনতে হবে? আলমারির এই চাবিনিরপেক্ষ দেরাজে আলো নেই, অন্ধকারও নেই। আত্মনিরোধের রশি দেয়াল টাঙিয়ে দিচ্ছে তুমি এবং তুমির মধ্যে। দৌড়ে চলে গেল কয়েকটা ধাঁধা মশকরা, বাদামি ইয়ার্কিতে ঢেকে যাচ্ছে চোখ।
আর খোলা ভেঙে শাঁস বের করে আনতে আনতে কেউ একটা ঘেমে উঠল। তুমি অথবা তোমার চাইতেও তীব্র ওপেক কোনও ছায়ার এই সুচ তোমার পিঠের ওপর কাঁথাস্টিচের ফোঁড় তুলেই যাচ্ছে। কফিনের ভেতর যাকে বন্ধ করে রেখেছ, সে তো শুধু গলার স্বর। এগ চিলি কয় যাহারে....নিন্দুকেরা কহিলো বটে তীরের মতো বাক্যি....বাস্তবে প্রতিটি নিন্দুক এক একখানি ঝানু তীরন্দাজ। তবে আহারের পরে মুখমণ্ডলে যে তৃপ্তির প্রভা দেখিয়াছি তাহাতে আমার মনে হইলো আমিও কি দিনে দিনে শ্রীমান পলাশ বর্মন হইয়া যাইতেছি। তবে আমার খাদ্য সেই কদ্দু আর সজিনার ডাঁটাই।বিষণ্ণ মনভার সকালের পাশে খুব আলগোছে এসে যে ভেজা পাতাটি বসেছিল আলোফোটার আগেই, তাকে বোলো এবছর একটিও শিউলি ছুঁইনি আমি। তবু তারই গন্ধ স্মৃতির ভিতর টুপটুপ হিমের শব্দে। কানে শুনিনি অথচ বুকের মধ্যে গানের সুরগুলো ঘুমোতে দেয়নি এবারেও। দ্যাখো, পায়ের অপারেশনের পর একটানা হাঁটতে পারি না কতদিন। অথচ মনে মনে যোজন পথ নদীতীর ধরে আমবাগানের পাশ দিয়ে রাধামাধবের মন্দির ছুঁয়ে ঠাকুরদালান অব্ধি দিব্যি যেতে পারি, নির্ভার। সেখানে ধূ ধূ কাশবনের দুলে ওঠার পাশে রঙ লাগছে কাদামাটির কাঠামোয়। অনন্ত ফ্রিজশটে থেমে আছে সময় ও স্থপতির মুখ সারিসারি! জানি সেই মুখগুলোর কেউই প্রায় নেই আর এখন। অথচ আছে। প্রত্যেকে। নেই হয়ে যাওয়া বিরাট বকুল গাছটার মতই অনুভবে ডালপালা শিকড়েবাকড়ে! খুব নির্জনতা ভিতর থেকে একা করে দেয় এখন। স্তব্ধও করে দেয় উৎসব আবহে। নেই অথচ আছ, আছ অথচ নেই---- এই দুই অপ্রকাশ্য ব্যথার আড়াল আলোড়িত করে প্রবল। স্পর্শাতীত দূরে চলে গেলে বিনিময়হীন অক্ষরমালার ওপর কেবল অসময়ের বৃষ্টিফোঁটা ঝরতেই থাকে।চলো, ভিজি। এখন তো তোমার অসুখ সম্পূর্ণ সেরে গেছে বাবি! তুমি ভালো আছ,বল? এসো, হাত ধরো---! দূূর্গা না, দুর্গা। পুজা না, পূজা। অঞ্জলী না, অঞ্জলি।ধর্মটা আপনার হইতে পারে, কিন্তু ভাষাটা আমারও মাতৃভাষা। এইটারে হেলাফেলা কইরেন না। আঁতে লাগে।
বিজ্ঞাপনের পাতায় কেন যে পিয়ানোর সন্ধানে এত ছানবিন, এত পুছতাছ! বরং ছেড়ে দাও একটা বেড়াল। বরং সে-ই খুবলে তুলুক দু-চারটে আঁশ। ছবির থেকে পিছলে যাচ্ছ তুমি, আর দেয়াল খুঁড়তে খুঁড়তে পিছলে যাচ্ছে শাবল। শুধু ঘুমের ভেতর একটা হাওয়া ঢুকে যাচ্ছে, আর অতিজাগরণের এই গুগলি খেলতে গিয়ে তোমার ব্যাট শূন্য থেকে টেনে নামাচ্ছে অম্লবৃষ্টি, অথচ তুমি বোধহয় জানতেও পারোনি, এতদিন তোমার গায়ের সঙ্গে সেঁটে যে দঁড়িয়েছিল, যাকে খুলতে খুলতে তুমি গুঁড়োগুঁড়ো করে ফেলেছ পিলসুজ থেকে পিচকারি অব্দি, সেও সম্ভবত তুমিই ছিলে আলমারির এই চাবিনিরপেক্ষ দেরাজে আলো নেই, অন্ধকারও নেই। আত্মনিরোধের রশি দেয়াল টাঙিয়ে দিচ্ছে তুমি এবং তুমির মধ্যে। দৌড়ে চলে গেল কয়েকটা ধাঁধা মশকরা, বাদামি ইয়ার্কিতে ঢেকে যাচ্ছে চোখ। আর খোলা ভেঙে শাঁস বের করে আনতে আনতে কেউ একটা ঘেমে উঠল। তুমি অথবা তোমার চাইতেও তীব্র ওপেক কোনও ছায়ার এই সুচ তোমার পিঠের ওপর কাঁথাস্টিচের ফোঁড় তুলেই যাচ্ছে।
ঝড় আসলে তোর খুব প্রেম পায়। জ্বর আসলে তোর খুব আম্মার হাত পায়। মনে হয় মাথায় কেন নাই ওই হাত। আবার জ্বর আসলে খুব জেদও ওঠে। এর মধ্যে এক বান্ধবীর কথা বলি। সে কইলো কথায় কথায় তার বর-এর সাথে সে বাইরে ঘুরতে গেছিলো। এর মধ্যে তার মিন্সট্রেশন শুরু হইসে। সে ভয়ে রেস্টুরেন্টে খেতেও পারতেসেনা, বসতেও পারতেসেনা। তো আমি বললাম তুই তর বররে বলবি না, আজব! সে কইলো, ও এসব পছন্দ করে না। খুব বকাবকি করে। শুনে আমি থ! এটাতে পছন্দ অপছন্দের কিছু তো আমার বোঝার বাইরে। নরমাল ব্যাপার। এতে সহযোগিতা করার চাইতে বেশি পছন্দ অপছন্দ ক্যামনে! তো জিজ্ঞেস করলাম, ক্যান তর বর পাঁঠা নাকি যে ন্যাচারাল প্রবলেম বুঝবে না? তো পাঁঠা শুনে আমার পাঁঠির খুব গায়ে লাগাতে সে ফোন রেখে দিলো।
এইবার আমার কথায় আসি। একদিন বিকালে খুব খারাপ লাগতেসিলো। আম্মা মারা যাবার পরপরই। তো আমার খুব কাছাকাছি ক্লোজফ্রেন্ড বলতে কমল ই থাকে। আমি কমলরে ফোন দিলাম। কমল বল্লো তুই দশ মিনিট পর বের হ, আমি বাসায় আসছি, ফ্রেশ হয়েই নামতেসি। বের হইলাম, এসে দেখি কমল ও চলে আসতেসে। আমরা চা খাইতেসি দাড়ায়া চায়ের দোকানে। এর মধ্যেই আমি বুঝলাম আমার শরীর খারাপ হইতাসে। তো আমি চা শেষ কইরা কমলরে বললাম দোস্তো, একটু বাসায় যেতে হবে। ও অবাক, বলে তুই আমাকে নামাইলি ক্যান তাইলে। দশ মিনিট হয় নাই। কাছাকাছি একটা রোম পুড়ে যাচ্ছে,তুমি নাই নাই করে উড়ে যাচ্ছে সমস্ত বুধবার।
বললাম একটু ঝামেলা হইসে। ঘাড়ত্যাড়ায় কয়, বল আগে কী হইসে, শুনি। বললাম আমার শরীর খারাপ হইসে, কোথাও বসা যাইতেসে না। ও প্রথমে বুঝে নাই, পরে নিজে দৌড়ায় গিয়ে প্যাড কিইন্যা আইন্যা দিসে। টোকিও স্কয়ারে গিয়ে আমি নিজে ঠিকঠাক হয়ে আমরা হাঁটলাম। এরপর ও আমাকে বাসা পর্যন্ত দিয়ে গেল। সিকিম যাবার পরেও এই ঘটনা। দাদা, আপারা আলাদা, খাবার হোটেল খুঁজতেসে গ্যাংটকে। আমি উপায় না দেখে দাদাকে কল দিলাম। আপা আর দুলাভাই ওয়াশরুমে। তো শাহরুখ খানভাই সেইখানে কোত্থেকে খুঁজে এনে দিলো। আমি এক হোটেলে গিয়ে চেঞ্জ করে নিলাম। এমনিতে শাহরুখ আমাকে সিমরন ডাকে। এর মানে ঘষেটি বেগম। কারণ সে কিছু করলেই আমি সেইটা পুরা গ্রুপে বলে দেই। সারাক্ষণ আমরা মারামারি করতেই থাকি। আরেকবার, ঝিগাতলায় একই ঘটনা। আমি নিজে গিয়ে কেনার অবস্থায় ছিলাম না। ঝিগাতলায় সলমানরা থাকে, তো সলমানকে ফোন দিয়ে বললাম, সে দৌড়াতে দৌড়াতে নিয়ে আসলো। ওইখানে একটা ক্যাফেতে গিয়ে আমি বাঁচলাম। এরা বন্ধু। এরা খাঁটি বন্ধু। আমার এদের নিয়ে প্রাইড হয়। যা বেসে বোঝাতে হয়,সে ভালোর কোন বাসা নেই, যে ভালোকে বুঝতে সব বাসা ছাড়া যায়, তাকে বাসতে হয় নাকি?
যে মানুষকে মাথায় তুইলা রাখবেন, তার প্রধান ও একমাত্র কাজ মাথায় দাঁড়ায়া কপালে লাত্থি আর চোউক্ষে গুতা দেওয়া। যে কোন সময় মুতে (ভদ্র ভাষায় সুসু ও হিসু পড়ুন) দিলেও বলার কিছুই...অ...আরেকখান কথা! আবেগ থেকে 'আ' ঝইরা যাওয়া মানুষের কেবল বেগ থাকে। আর এই সমস্ত চাপ সামলানো মানুষগুলা একটু হাসলেই কত কত জনের পিত্তি জ্বইলা যায়! পিত্ত পোড়া মানুষের হজমে সমস্যা হবেই, নতুন কিছু না..জনস্বার্থে ট্যান্টানায়ায়ায়া....
যাঁদের স্যানিটারি ন্যাপকিন শুক্রবার বেরিয়েছে, অথচ এখনো পাননি। উদ্বিগ্ন হবেন না। শনি/রবি দুদিন ছুটি থাকায় দেরি হচ্ছে। এই দেরি সম্পূর্ণ রূপে অফিস সংক্রান্ত বিষয়।যে বিলের ছবি দেওয়া হয়েছে, সেখানে ট্র্যাকিং নাম্বার রয়েছে। অনুগ্রহ করে একটু ট্র্যাকিং করে অবস্থান জেনে নেবেন। তার জগতে, তার ঈশ্বরের জগতে, আমি দুদণ্ড বসতে এলাম পার্কে অপ্রয়োজনীয় লিঙ্গমূর্তি সে অফিসে গেছে, তার জগতের চাবি রেখে গেছে বলেছে মাঝে মাঝেই মনেও করিয়ে দেবে, সে ছিল, সে আছে আস্তিকের যেমন বিশ্বাস নাস্তিকের শুকনো নিঃশ্বাস তার বাগানের ফুলে ফেলে ফেলে আমি ক'মিনিট বসতে এলাম এই যে শহর, কখনো কখনো অন্ধের মতোন একজন মানুষকে বিশ্বাস করলে, একটা সময় সূর্যের ফকফকা আলোতেও অন্ধকারাচ্ছন্ন কুয়াশা ছাড়া কিছুই দেখতে পাওয়া যায় না। কারণ, মানুষ যেমন ভালোবাসে আবার এই ভালোবাসার ছলে ঠকিয়েও দেয় কেউ ধরতে পারে কেউ পারে না ।..
এই উপুড় শহর, তাতে লিভারে উঠলে ব্যথা সে আমায় ডাকে আস্তিকের যেমন বিশ্বাস বলে যে যেমন খুশী ওষুধ লিখলে আমি, পিয়ন পাঠিয়ে তখনি আনিয়ে নিয়ে নির্দ্বিধায় খাবে আস্তিকের যেমন বিশ্বাস আমি কত কত ঘরে অশোক সরিষামুঠি খুঁজে ফিরি শিশুটির নিরাময় তরে আমি যাই গুগলেরও কাছে বলো সেই অসুখের আরোগ্য আছে? সে তো সেই বিধুর প্রেমিক সেই সেভারাস স্নেপ হঠাৎ টেক্সট এ বলে বালকের চোখ তার মায়ের মতন হঠাৎ টেক্সট এ বলে, আশীর্বাদ করবে শিশুকে! আমরা ইউ নো হু-র ভীষণ বিরোধী লড়তে লড়তে আর দৈবী বাগানের দূরে যেতে যেতে আশীষের ফুলটুকু মাথায় ছুঁইয়ে দিয়ে ডায়েরির পাতায় রেখে দিই নাস্তিকের যেমন বিশ্বাস সারা গায়ে জেগে ওঠে মেঘের মতো সুদৃশ্য ছত্রাক। ধবধবে টেবিলক্লথে ছলকে পড়া কফিদাগ মন। খুলে রাখা, ভুলে যাওয়া কলমের কালি মেখে চাইছে দু’চোখ। শিরা বেয়ে হাতে নেমে যেদিকে যা ছুঁই− বিছানার চাদর, হিসেবের খাতা, ইরটিক বই − এ শহরে দিন কাটে, চারিদিকে ওড়ে শুধু কালোকালো ছোপ। পা বেয়ে শরীরে ঘুমোতে যায় উল্কিস্মৃতি, আমার প্রিয় শহর। রোজ রাতে একে একে লাইন করে সাজানো হয় ফুটপাথ। আঁটোসাঁটো পোষাক, মুখ বাঁধা, ভেতরের কথা যেন বেরিয়ে না আসে। সারি সারি কালো নীল সবুজের গারবেজ ব্যাগ। রাতারাতি পাচার হয়, শহরের নিকোনো উঠোন। এসবের নীচে চাপা পড়ে থাকে বহু সংসার। ছেঁড়া দস্তানা, কুড়োনো টয়েলেট পেপার, ভাঙা কাপ, খুচরো সেন্ট, আধপোড়া সিগারেট, গোলাপী খরগোশ। যে মানুষ ঘরছাড়া, আবর্জনার শেষে তার প্লাস্টিক বাড়ি। প্রতিরাতে হানাদার ফাঁকি দিয়ে পলাতক বাড়ি দেখি সকালের ট্রেনে। শহরের সূর্যমুখী ক্ষত সারাদিন বাঁচে, মরে রোজ রাতে। রাত্রি হ’লেই সব ঝকঝকে, তকতকে।
সব জলোচ্ছ্বাস ফিরে গেলে শুধু পদচিহ্ন থেকে যাবে উঠোনে, বারান্দায়, আর ঘরের একাকী মেঝেতে। দুলে দুলে বাতাসে ভাসবে শরতের সাদা কাশফুল আর সাদা ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘেরা ঘুরে ঘুরে কবিতা পড়বে সারাটা কাশময়।নিবিড় সে সন্ধ্যেবেলায়, চৌকাঠে ঝরিয়ে টুপটাপ শিউলি শরীর তুই বলবি, যাই নি তো কোত্থাও, এই দ্যাখ, ঘ্রাণ হয়ে রয়ে গেছি তোর প্রতিটি নিঃশ্বাসের ভিতর। ছাইরঙ টিশার্টের ভেতর ঘন অন্ধকার অভিমান ধীরে ধীরে অনুরাগ জোছনা হয়ে উঠবে সারাটা আলমারি জুড়ে। এমন করেই রাত থেকে ভোর হবে, বুকের দূর্বাঘাসে শিশির ঝরবে টুপ টাপ। বিসর্জনই দেখেছিলে হে মন, অথচ কী ভীষণ সত্যি ছিল প্রতিটি আরাধনা ক্ষণ।ভালবাসলে নাকি নদী কথা বলে! আমি ভালবাসার জন্য সপ্ত নদীর ধারে হেঁটে চলেছি অবিরত স্রোতে ভেসেও চলেছি তবু নদী কথা বলেনি ভালবাসলে নাকি পাথরে ফুল ফোটে আমি ভালবেসে অহল্যা হয়েছি ফুল ফোটার বদলে পাথর হয়ে অপেক্ষায় ভালবাসলে নাকি বৃষ্টি নামে আমি বৃষ্টি ভিজব বলে পথে শরীর ঝলসে গেছে তবু বৃষ্টি নামেনি এরপরেও তুমি বলবে প্রেমের গান লেখ! তবে আমার ধারণা, এও কোন 'জংগল গাছ'ই হবে, আমি সাধারণত: কোন তথাকথিত জংগলি গাছ বা আগাছা উপড়ানোয় ঘোরতর আপত্তি জানিয়ে থাকি, এটাও সেরকম কিছুই হবে, এবার আজ এসব অদ্ভুতদর্শন বীজ, ফল দেখে কী গাছ, কবে এল, এসব প্রশ্নবাণে খোঁচায়িত হয়ে বল আমার কোর্টে ঠেলে দিলেন!
মূল প্রসঙ্গে আসি। আমিও স্কার্ট পরা বা লেগিংস সামান্য তোলা ছবি এক/দু’বার দিয়েছি। তাই বলে কেউ কেউ হয়ত মনে করেন যে নিয়মিত খুব সংক্ষিপ্ত পোশাকের ছবি না দিলে ‘নারীবাদ’ সম্ভব নয়, তেমনটা আমি ভাবি না। আমার আরো দু’টো লক্ষী মেয়ে আছে। সুরভি আর সুবাসিনী । ওরা পশ্চিমে থাকে। খুব মেধাবী ও পরিশ্রমী । ওরা কিন্ত ‘দ্যাখো, নারীবাদী হলে ইহা ইহা পরিতে হয়’ বলে পশ্চিমা পোশাকে ছবি দেয় না। ওরা পশ্চিমে ওদের সমুদ্রতীরের স্বাভাবিক যেসব ছবি দেয় সেসব ছবির কোনো কোনোটির পোশাক আমাদের দৃষ্টিতে ‘সংক্ষিপ্ত’ হলেও আমাকে বিরক্ত করেনি। কারণ আমি জানি সুরভি বা সুবাসিনী কেউই নিজেকে ‘নারীবাদের আইকন’ প্রমাণে এগুলো পরছে না। পশ্চিমবঙ্গের অনেকের কাছে 'বাঙাল ভাষা'টা এখনই বেশ একটা একজোটিক ভাষা । অনেকে বেশ মজা পায় ভাষাটা শুনলে। যেন দূর দেশের ভাষা এটি, যেন অচেনা কিছু। ঘটিরা রিলেট করতে পারে না। পূর্ব বঙ্গ থেকে আসা লোকেরা রিলেট করতে পারে বটে, তবে তাদের ছেলেমেয়েরা অনেকটাই কম পারে, নাতিপুতিরা তো পারে না বল্লেই চলে। দিন যত যাবে, তত তাঁরা গত হবেন , তত এই ভাষাটা আরো বেশি অন্য দেশের, অন্য কালচারের, অন্য ধর্মের, অন্য মানুষের ভাষা হয়ে উঠবে। কলকাতার বাঙালি মুসলমানরা বাঙাল ভাষায় কথা বলে না। মু্সলমানদের সংগে মেলামেশা না করা বাঙালি হিন্দুর কাছে মুসলমান মানেই একজোটিক, যে ভাষায় তারা কথা বলে, সে ভাষায় একজন মুসলমান কী করে কথা বলবে? এই ভাষা তো হিন্দুদের। মুসলমান হয় উর্দু বলবে, নয়তো 'বাংলাদেশের ভাষা' বলবে। কলকাতায় আমার বাঙালি মুসলমান বন্ধুরা এমনই ভয়ঙ্কর বাঙালি এবং এমনই প্রচণ্ড ঘটি যে বাস কে বাশ বলে, শশিকে ছছি বলে। মর্ত্যের দেবীরা ভালো নাই ;জীবন কেটে কেটে বিক্রি করে আমাকে, টুথপেস্ট আঁকা শহরে তবু দাগের মতো ফিরি করি ভালোবাসা । একদিকে রোহিত আর একদিকে স্মিথ ; গ্রেটেস্টরাই ডবলের পর ডবল করে..দ্বিপ্রাহরিক হাওয়া এসে পিঠে টোকা মারে হু হু স্বরে বলে, 'ভালো আছো?' বসন্তের দিন বুঝি শুরু হ'লো,এইবার--, বুক জুড়ে জেগে ওঠে দিনাবসানের গান, জেগে ওঠে ছোটো বড় নানা অভিযোগ, হাওয়া শোনে না সেইসব, পথচারী ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলে যায় দূরে, দূরান্তরে আরেকজনের পিঠে হাত রাখে,আনুপূর্বিক স্বরে বলে, ' ওহে কেমন আছো?'
 জয়িতা ভট্টাচার্য | 27.58.255.50 | ১০ আগস্ট ২০২১ ১৯:৩৪734850
জয়িতা ভট্টাচার্য | 27.58.255.50 | ১০ আগস্ট ২০২১ ১৯:৩৪734850জয়িতা ভট্টাচার্য নিয়েছেন মলয় রায়চৌধুরীর সাক্ষাৎকার
জয়িতা : কবিতা না গদ্য-- গদ্যের ক্ষেত্রে প্রবন্ধ না গল্প-উপন্যাস ---তুমি নিজে কোনটা লিখতে বেশি পছন্দ করো।
মলয় : আমার নিজের তেমন কোনো প্রেফারেন্স নেই । নির্ভর করে মগজের ভেতরে একটা বিশেষ সময়ে কি ঘটছে । প্রবন্ধ লিখি মূলত সম্পাদকদের অনুরোধে । এখন আর প্রবন্ধ লিখতে ভালো লাগে না, প্রাবন্ধিকের সংখ্যা কম বলে সম্পাদকরা প্রবন্ধ চান, এমনকি সম্পাদক নিজে কোনো বিষয় বেছে নিয়ে লিখতে বলেন। তা কি পারা যায় ? এখন তেমন পড়াশোনা করতে বা সমাজ নিয়ে ভাবতেও ভালো লাগে না । ফিকশান লিখি, কোনো একটা ব্যাপার স্ট্রাইক করলে লিখতে থাকি, অভিজ্ঞতায় তো মাল-মশলার অভাব নেই, নিজের জীবন থেকে কতো চরিত্র তুলে আনা যায় । কেউ চাইলে দিই । কবিতা তো অ্যাডিকশান, যখন নেশাটা পেয়ে বসে তখন না লিখে নিস্তার নেই । সেগুলোও ইমেলের বডিতে লিখে রাখি, কেউ চাইলে পাঠাই , আমার মনে না ধরলে ডিলিট করে দিই। ইন ফ্যাক্ট যে চায় তাকেই পাঠাই, কোনো বাদ বিচার করি না। অনেকে বিষয়বস্তু বলে দেন, তখন গোলমালে পড়ি, কেননা আমি তো বিষয়কেন্দ্রিক কবিতা লিখি না ; নিজের ইচ্ছেমতন লিখি, কারোর পছন্দ হোক বা নাহোক । কবিতার খাতা বলে আমার কোনো ব্যাপার নেই, ২০০৫ সালের পর থেকে, অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টির পরে ভুল ওষুধের দরুন আরথ্রাইটিস হল । , তারপর হাঁপানিতে ধরল, হার্নিয়া, প্রোস্টেট, ভেরিকোজ ভেইনস । আরথ্রাইটিসের কারণে লেখালিখির বাইরে চলে যাচ্ছিলুম, সে কষ্ট তুই বুঝতে পারবি না । মগজের ভেতরে লেখার ঘুর্ণি হয়ে পাক খাচ্ছে অথচ কিছুই লিখতে পারছি না । তারপর মেয়ের উৎসাহে কমপিউটার শিখলুম, বাংলা টাইপ করতে শিখলুম, ডান হাতের মধ্যমাটা কম আক্রান্ত, সেটাই টাইপ করতে ব্যবহার করি । ছেলে এই কমপিউটারটা দিয়ে গেছে, ছুটিতে এলে পরিষ্কার করে দিয়ে যায় । মাঝে তো তিন-চার বছর লেখালিখি করতেই পারিনি আঙুলের সমস্যার জন্য ।
জয়িতা : তোমার বিভিন্ন উপন্যাস পড়লে দেখা যায় প্রতিটির ন্যারেটিভ টেকনিক ও আঙ্গিক এ ভিন্নতা । ‘ডুবজলে যেটুকু প্রশ্বাস’ থেকে ‘জলাঞ্জলি’, ‘নামগন্ধ’, ‘ঔরস’, ‘প্রাকার পরিখা’, সবগুলো একই চরিত্রদের নিয়ে এগিয়েছে, একটাই উপন্যাস বলা যায় তাদের, কিন্তু তুমি প্রতিটির ফর্ম আর টেকনিকে বদল করতে থেকেছো । কেন ? তারপর, ‘অরূপ তোমার এঁটোকাঁটা’ উপন্যাসে গিয়ে সম্পূর্ণ নতুন টেকনিক প্রয়োগ করলে, তিন রকমের বাংলা ভাষার খেলা দেখালে। ‘নখদন্ত’ উপন্যাসে বেশ কয়েকটা ছোটোগল্প আর নিজের রোজনামচার অংশ ঢুকিয়ে দিয়েছ । এই বিষয়ে কিছু বলো । এটা কি সচেতন প্রয়াস?
মলয় : হ্যাঁ । পাঁচটা মিলিয়ে একটা অতোবড়ো উপন্যাস তো কেউ ছাপতো না, তাই বিভিন্ন সময়ে আলাদা-আলাদা করে লিখেছিলুম । ‘ডুবজলে’ উপন্যাসটা সহকর্মীদের নিয়ে লেখা, ক্রমে জানতে পেরেছিলুম যে কয়েকজন গোপন মার্কিস্ট-লেনিনিস্ট । পাঁচটা আলাদা উপন্যাস লিখতে পেরে একদিক থেকে ভালোই হলো, সব কয়টায় নতুনত্ব আনতে চেষ্টা করেছি । ব্যাপারটা মগজে এলে বেশ কিছুকাল ভাবি আঙ্গিক নিয়ে, উপস্হাপন নিয়ে, তারপর লেখা আরম্ভ করি । অনেক সময়ে লিখতে লিখতে আপনা থেকেই একটা আঙ্গিক গড়ে ওঠে, যেমন ‘নখদন্ত’ বা ‘অরূপ তোমার এঁটোকাঁটা’ । ‘নখদন্ত’ বইটার জন্য পশ্চিমবঙ্গে ট্যুর করার সময়ে চটকল আর পাটচাষ-চাষিদের নিয়ে প্রচুর তথ্য যোগাড় করেছিলুম । তেমনিই ‘নামগন্ধ’ লেখার সময়ে পশ্চিমবঙ্গের আলুচাষি আর কোল্ড স্টোরেজের তথ্য সংগ্রহ করেছিলুম । এই বইদুটোয় বেশ কিছু চরিত্র চোখে দেখা । অভিজ্ঞতার বাইরেও লিখেছি, যেমন ‘জঙ্গলরোমিও’, একদল ক্রিমিনালের বিস্টিয়ালিটি নিয়ে । টানা একটামাত্র বাক্যে ফিকশান লিখেছি ‘নরমাংসখোরদের হালনাগাদ’, এটাও জাস্ট ইম্যাজিনেটিভ, পশ্চিমবাংলার রাজনৈতিক বিভাজন নিয়ে । ‘হৃৎপিণ্ডের সমুদ্রযাত্রা’ রবীন্দ্রনাথের দাদুর দেহ ইংল্যাণ্ডের কবর থেকে তুলে হৃৎপিণ্ডে কেটে কলকাতায় নিয়ে আসার কাহিনি, রবীন্দ্রনাথ আর রবীন্দ্রনাথের বাবারও সমালোচনা করেছি ফিকশানটায় । রবীন্দ্রনাথের দাদু যদি আরও দশ বছর বাঁচতেন তাহলে পশ্চিমবাংলার ইনডাস্ট্রি উন্নত হতো । সেসময়ে ওনাকে ফালতু বাঙালিরা আক্রমণ করেছিল চরিত্রের দোষ দিয়ে অথচ এখনকার ভারতে প্রতিটি পুঁজিপতি ওনার তুলনায় হাজারগুণ চরিত্রদোষে দুষ্ট, এমনকি তাদের মধ্যে জোচ্চোর, কালোবাজারি, চোরাইমালের কারবারি, দেশ ছেড়ে পালানো বজ্জাতরাও আছে । ডিটেকটিভ উপন্যাসটা লিখেছিলুম চ্যালেঞ্জ হিসেবে, কিন্তু সেটাতেও আমি ভারতের সমাজকে টেনে এনেছি । রাজনীতি আর সমাজকে বাদ দিয়ে উপন্যাস লিখতে পারি না, দীর্ঘ গল্প ‘জিন্নতুলবিলাদের রূপকথা’ জীবজন্তু-পাখিদের নিয়ে, কিন্তু তাও পশ্চিমবাংলার রাজনৈতিক ঘটনাবলী আর চরিত্রদের নিয়ে । ‘রাহুকেতু’ উপন্যাসটা হাংরি আন্দোলনের সময়ের জীবনযাপন নিয়ে । ‘আঁস্তাকুড়ের এলেক্ট্রা’ বাবা আর মেয়ের যৌন সম্পর্ক নিয়ে । নেক্রোফিলিয়া নিয়ে লিখেছি ‘নেক্রোপুরুষ’, সময়ের স্হিতিস্হাপকতা নিয়ে লিখেছি ‘চশমরঙ্গ’ ।
জয়িতা : পোষ্টকলোনিয়াল বা কমনওয়েল্থ লিটেরেচারের ক্ষেত্রে সলমন রুশডিকে আদর্শ পোস্টমডার্ন নভেলিস্ট বলে কি তুমি মনে করো ?
মলয় : রুশডি একজন ম্যাজিক রিয়্যালিস্ট ঔপন্যাসিক, মার্কেজ প্রভাবিত । যতোই জটিল হোক, পাঠক ঠিকই বুঝতে পারে, যেমন ‘স্যাটানিক ভার্সেস’-এর ক্ষেত্রে । আমেরিকার আলোচকরা ম্যাজিক রিয়্যালিজমকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে চায় না, কেননা টেকনিকটা তাদের দেশে গড়ে ওঠেনি, তাই ম্যাজিক রিয়্যালিস্ট লেখকদেরও পোস্টমডার্ন বলে চালাবার চেষ্টা করে । পোস্টমডার্ন উপন্যাসের কিছু সূক্ষ্ম উপাদান থাকলেও রুশডির ফিকশানকে পোস্টমডার্ন তকমা দেয়া উচিত হবে না । গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজকে পোস্টমডার্ন বললে স্প্যানিশ আলোচকরা বুল ফাইটের ষাঁড় লেলিয়ে দেবে ।
জয়িতা : তোমার গদ্যে প্রথাগত প্রেম আসেনা । নেই স্টিরিওটাইপ প্রটাগনিস্ট । সেটা কি সচেতন ভাবে পরিহার করেছো স্বকীয়তা আনতে? ‘ডুবজলে যেটুকু প্রশ্বাস’ উপন্যাসে মানসী বর্মণ, শেফালি, জুলি-জুডি ; ‘নামগন্ধ’ উপন্যাসে খুশিরানি মণ্ডল, ‘অরূপ তোমার এঁটোকাঁটায়’ কেকা বউদি, ‘ঔরস’-এ ইতু, এরা একজন আরেকজনের থেকে পৃথক এবং কেউই স্টিরিওটাইপ নয় । এমনকি উপন্যাসের শেষে চমক দিয়েছ যে খুশিরানি মণ্ডলকে পূর্ববঙ্গ থেকে তুলে আনা হয়েছিল, সে প্রকৃতপক্ষে জনৈক মিনহাজুদ্দিন খানের নাতনি । আত্মপরিচয় নিয়েও খেলেছো খুশিরানি মণ্ডলের ক্ষেত্রে, সে নিজের উৎস না জেনেই লক্ষ্মীর পাঁচালী পড়ে, ব্রত রাখে, চালপড়ায় বিশ্বাস করে । মলয়রচনার আঙ্গিক সম্পর্কে আরেকটু বিস্তারিত জানতে চাইবো ।
মলয় : তার কারণ আমি প্রথাগত প্রেম করিনি আর দ্বিতীয়ত উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র ব্যাপারটা ইউরোপ এনেছিল, মেট্রপলিটান সিংহাসনের প্রতীক হিসাবে । বয়সে আমার চেয়ে বড়ো নারীরা আমার জীবনে প্রথমে প্রবেশ করেছিলেন । তাই হয়তো যুবকের চেয়ে যুবতীর বয়স বেশি হয়ে যায়। নারী চরিত্রগুলোয় আবছাভাবে কুলসুম আপা আর নমিতা চক্রবর্তীর উপস্হিতি রয়ে যায় । হাংরি আন্দোলনের সময়ে যে যথেচ্ছ জীবন কাটিয়েছি, তার ছাপও নারী চরিত্রদের ওপর রয়ে গেছে । খুশিরানি মণ্ডলের মাধ্যমে দেখিয়েছি যে নিজের আইডেনটিটি ব্যাপারটা কতো গোলমেলে । এখনকার ভারতীয় সমাজের দিকে তাকিয়ে দ্যাখ, আইডেনটিটি পলিটিক্সের দরুন সমাজ ভেঙে পড়ছে, প্রতিনিয়ত লাঠালাঠি হচ্ছে, দলিতদের পেটানো হচ্ছে, মুসলমানদের ঘরছাড়া করা হচ্ছে । গোরুর মাংস খাওয়া বন্ধ করে দিয়ে কতো লোকের জীবিকা নষ্ট করা হয়েছে । ইসলামে শুয়োর মাংস নিষিদ্ধ, কিন্তু দুবাইয়ের মলগুলোয় শুয়োরের মাংস বিক্রির আলাদা এলাকা আছে । আইডেনটিটি পলিটিক্স থেকে আমরা পৌঁছে গেছি জিঙ্গোইজমে । আমার বিয়ের কথা বলি ; আমি সলিলাকে বিয়ে করেছি তিন-চার দিনের আলাপের মধ্যেই, দুজনে দুজনকে হঠাৎই ভালো লেগে গিয়েছিল। এই নিয়ে একটা দীর্ঘ স্মৃতিকথা লিখছি, ‘আমার আজব বিয়ে’ নামে, অজিত বলেছে বই হিসেবে বের করবে । সলিলার মা-বাবা ছোটোবেলায় মারা গিয়েছিলেন ; তাই শাশুড়ির আদর খাবার সুযোগ হলো না আমার ।
জয়িতা : ‘ডুবজলে’ উপন্যাসে টেবিলের ওপরে রাখা মানসী বর্মণের পাম্প দিয়ে বের করা দুধ অতনু চক্রবর্তী টুক করে চুমুক দিয়ে খেয়ে নিয়েছিল । এটা কেন ?
মলয় : অতনুর মা সম্প্রতি মারা গিয়েছিলেন, সে কয়েকমাস মিজোরামে জুলি-জুডি নামে দুই সৎবোনের সঙ্গে যৌনজীবন কাটিয়ে পাটনায় ফিরে মানসিক গুমোটের মধ্যে আটক হয়ে গিয়েছিল। দুধটা দেখে আপনা থেকেই মায়ের অনুপস্হিতি তার মনে কাজ করে ওঠে । পরে ‘ঔরস’ আর ‘প্রাকার পরিখা’ উপন্যাস দুটোয় মানসী বর্মণ আর অতনু চক্রবর্তীর জটিল যৌন সম্পর্ক গড়ে ওঠে, ওরা তখন ঝাড়খণ্ডে মাওবাদী জমায়েতে যোগ দিয়েছে ।
জয়িতা : বাংলা সাহিত্যে বিশ্বায়নের প্রভাব কতটা প্রতিফলিত বলে তোমার মনে হয় ? বিশ্বায়নের রেশ ফুরিয়ে যাচ্ছে বলে মনে হয় তোমার ?
মলয় : এখনকার ব্যাপারটা বলতে পারব না । আমি আর বিশেষ পড়াশুনার সময় পাই না । বুড়ো-বুড়ি মিলে সংসার চালাতে হয় বলে সময়ের বড্ডো অভাব, বাজার করা, ঝাড়-পোঁছ, কুটনো কোটা, রান্নায় হেল্প ইত্যাদি । বিশ্বায়নের পর যে সব বাংলা উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে তার কিছুই প্রায় পড়িনি, বিশ্বায়ন তো বলতে গেলে ব্রেক্সিট আর ট্রাম্পের গুটিয়ে ফেলার রাজনীতির দরুন উবে যেতে বসেছে, কেবল চীনই আগ্রহী ওদের মালপত্তর বিক্রির জন্য, আমাদের দেশের বাজার প্রায় কবজা করে ফেলেছে চীন । তবে ঔপনিবেশিক বাংলা সাহিত্য তো ইউরোপের অবদান । বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস লেখা আরম্ভ করেছিলেন ইউরোপীয় ফর্মে । মাইকেল অমিত্রাক্ষর আরম্ভ করেছিলেন ইউরোপের ফর্মে । তিরিশের কবিরা কবিতা লেখা আরম্ভ করেছিলেন ইউরোপের ফর্মে, এমনকি জীবনানন্দের কবিতায় ইয়েটস, বিষ্ণু দের কবিতায় এলিয়টের উপস্হিতি খুঁজে পান বিদ্যায়তনিক আলোচকরা । ব্রিটিশরা আসার আগে আমাদের সাহিত্যধারা একেবারে আলাদা ছিল । প্রতীক, রূপক, চিত্রকল্প, মেটাফর ইত্যাদি ভাবকল্পগুলো তো ইউরোপের অবদান । আধুনিক সঙ্গীত সম্পর্কে আমার জ্ঞান নেই, কিন্তু অনেকে রবীন্দ্রনাথের গানে ইউরোপের প্রভাব পান, এমনকি হুবহু গানের সুরের নকল । কবির সুমন আসার পর গানে রদবদল হলো।
জয়িতা : শূন্যদশকের কবি সাহিত্যিকদের কাছেও পুনরাধুনিক ,উত্তরাধুনিক বা আধুনান্তিক সাহিত্য সম্পর্কে ধোঁয়াশা। এর কারণ কি বলে মনে হয় ? বাংলা সাহিত্য সামগ্রিকভাবে আজকের বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে কতটা সমান্তরাল ?
মলয় : ধোঁয়াশা হলেও তাদের লেখায় ছাপ পাওয়া যাবে । আর সকলেরই মগজে ধোঁয়া ঢুকে আছে বলা যাবে না । অনেকে যথেষ্ট শিক্ষিত । আবার অনেকের আগ্রহ নেই, তারা নিজের মতো করে লিখতে চায় । পুনরাধুনিক, উত্তরাধুনিক, অধুনান্তিক, স্ট্রাকচারালিজম, পোস্টস্টাকচারালিম, ফেমিনিজম সম্পর্কে না জেনেও দিব্বি লেখালিখি করা যায় । কবিতা সিংহ তো ফেমিনিজমের তত্ব না পড়েও ফেমিনিস্ট কবিতা লিখে গেছেন । বাংলা কমার্শিয়াল পত্রিকায় এখন যে ধরনের মিল দেয়া কবিতা লেখা হয়, ইউরোপে আর তেমন কবিতা লেখা হয় না, ওদের কবিতায় ছবির ভাঙন অনেক বেশি আর দ্রুত । প্যারিস রিভিউ আর পোয়েট্রি পড়লে দেখা যায় যে অনেকে সহজ ভাষায় কবিতা লিখছেন, জটিলতা বর্জন করে, যখন কিনা বাংলায় বহু তরুণ কবিতাকে জটিল করে তুলছেন । আসলে কবিরা লেবেল পছন্দ করেন না । সকলেই চায় তাকে তার নামে লোকে জানুক, লেবেলের ঘেরাটোপে নয় । আমি নিজেই হাংরি লেবেলের দরুন বিরক্ত বোধ করি । বহু পাঠক তো ‘প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার’ ছাড়া কিছুই জানে না।
জয়িতা : একটু ব্যক্তিগত প্রশ্নে আসি । ‘ছোটোলোকের ছোটোবেলা’ ও ‘ছোটোলোকের যুববেলায়’ নিজের বড়ো হয়ে ওঠার কথা লিখেছো । হাংরি আন্দোলনের সময়কার ঘটনাগুলো ‘হাংরি কিংবদন্তি’ ও ‘রাহুকেতুতে’ লিখেছ । কিন্তু পরবর্তী পর্বের মলয় রায়চৌধুরী বেশ কিছুকাল অপ্রকাশিত । এই সময়টার কথা বলো । সত্যি কি লেখোনি না লিখেছ তা অপ্রকাশে । এই ট্রান্সিশনাল সময়টার কথা বলো।
মলয় : লিখেছি তো, সবই লিখেছি । ‘আখর’ পত্রিকার সাম্প্রতিক সংখ্যায় লিখেছি “ছোটোলোকের জীবন” শিরোনামে । ওটা প্রতিভাস থেকে “ছোটোলোকের সারাবেলা” নামে প্রকাশিত হবার কথা । ‘ছোটোলোকের জীবন’ তোকে পাঠিয়েছি, পড়ে দেখিস । অমিতাভ প্রহরাজ লিখেছে ‘আখর’ ওই সংখ্যাটা লোকে গান্ধী জয়ন্তীর আগের দিনে রামের বোতল কেনার মতন কিনেছিল ।
জয়িতা : ব্যক্তি মলয় ও লেখক মলয়ের মধ্যে ফারাক কতটা? তুমি নিজেকে কিভাবে দ্যাখো ।
মলয় : কোনো তফাত আছে বলে মনে হয় না, তবে আমি ব্যক্তি মলয়ের ইমেজ ভাঙার চেষ্টা করি, কেবল ভাষা ভেঙে হাত গুটিয়ে বসে থাকি না । আমিও যেকোনো লোকের মতন বাজার যাই, দরাদরি করি, যৌবনে মেছুনির সঙ্গে ফ্লার্ট করতুম, কয়েক মাস আগে পর্যন্ত সন্ধ্যাবেলা সিঙ্গল মল্ট খেতুম, সিরোসিসের সিম্পটম দেখা দিয়েছে বলে আর খাই না । হাংরি আন্দোলনের সময়ে গাঁজা চরস আফিম এলএসডি বাংলা খেতুম, এখন আর খাই না । বাড়িতে যে পোশাক পরে থাকি সেটাই অতিথিদের সামনেও পরে থাকি, মহিলারা এলেও । কথা বলার ধাঁচেও কোনো তফাত নেই, যদিও বেশ কিছু সাহিত্যিককে দেখেছি কেমন ক্যালাটাইপের গলায় কথা বলতে । তারা সব বুদ্ধদেব বসুর ছাত্র বা ছাত্রদের ছাত্র । আমি হুগলির বুলিতে ইমলিতলা মিশিয়ে চালিয়ে যাই । ব্যক্তি আর লেখক দুইই ইমলিতলার, তাই সহজেই নিজের ইমেজ ভাঙতে পারি ।
জয়িতা : তোমার সমসাময়িক কোনো সাহিত্যিকের কথা বলো যাঁর সঠিক মূল্যায়ন কলকাতা কেন্দ্রিক সাহিত্য গোষ্ঠি করতে পারেনি যথাযথ ।
মলয় : মূল্যায়নই হয় না, তো আবার সঠিক মূল্যায়ন । এতো বেশি সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক গোষ্ঠীবাজি হয় যে বেশির ভাগ প্রতিভাবান লেখক-কবির মূল্যায়ন হয় না, বিশেষ করে যারা গদ্য নিয়ে কাজ করছে তারা অবহেলিত থেকে যান । পুরস্কারগুলো নিয়ে টানাটানি হয় । সিপিএমের লোকেদের বাংলা অকাদেমি থেকে বিদেয় করে দেয়া হলো ওই একই সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক কারণে, তাঁরাও জ্ঞানী-গুণী ছিলেন । এখন একদল নতুন মুখ এসেছেন যাঁরা তাঁদের প্রিয় সাহিত্যিক আর সংস্কৃতিকর্মীদের কাঁধে উত্তরীয় দিচ্ছেন । যারা দুটো দিককেই এড়িয়ে গেছে তাদের প্রতিষ্ঠান গুরুত্ব দেয় না । যেমন কেদার ভাদুড়ি, সজল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখকে ।
জয়িতা : জীবনের ইমনকল্যাণে এসে তোমার চেতনায় কোনো পরিবর্তন এসেছে ? জীবনদর্শনের ক্ষেত্রে বলছি।
মলয়: এখন আমার একাকীত্ব ভালো লাগে, বেশি কথা বলতে ভালো লাগে না, আমার স্ত্রীও বেশি কথা বলা পছন্দ করে না । আমরা কোনো অনুষ্ঠানে যাই না । খাবার নেমন্তন্ন এড়িয়ে যাই, শরীরের কারণে । এখানে মুম্বাইতে আত্মীয় বলতে আমার এক মামাতো ভায়রাভাই, যার বয়স আমার চেয়ে ছয় বছর বেশি । কিন্তু এও মনে হয় যে মরার পর শ্মশানে নিয়ে যাবার লোক জোটানো বেশ কঠিন হবে । মাকে যেখানে দাহ করা হয়েছিল সেখানেই পুড়তে চাই । নয়তো বেস্ট হবে দেহ দান করে দেয়া । সেটা মরার পর বডির অবস্হা কেমন থাকে তার ওপর নির্ভর করে । আমার স্ত্রীর আপত্তি নেই । স্ত্রী আগে মারা গেলে আমারও আপত্তি নেই । ভীতিকর হলো যে আরথ্রাইটিসের জন্য সই করতে পারি না, স্ত্রীকে সই করতে হয়, সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হয় ব্যাঙ্কে ।
জয়িতা: তোমার জীবন ও সাহিত্যচর্চার ওপর দেশে বিদেশে গবেষণা হয়। সে সম্পর্কে কলকাতার পাঠক মহল জানতে চায় ।
মলয়: বছর দশেক আগে থেকে আরম্ভ হয়েছে । প্রথম পিএইচডি করেছিলেন বিষ্ণুচন্দ্র দে আর এমফিল করেছিলেন স্বাতী ব্যানার্জি । আমেরিকা থেকে মারিনা রেজা এসে হাংরি আন্দোলন নিয়ে গবেষণা করে গেছেন, এখন গুটেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে করছেন ড্যানিয়েলা লিমোনেলা, রূপসা বসু নামে একটি মেয়ে এমফিল করছে, প্রবোধচন্দ্র দে এম ফিল করছেন, নয়নিমা বসু, নিকি সোবেইরি, বিবিসির জো হুইলার, ফরজানা ওয়ারসি, জুলিয়েট রেনোল্ডস, শ্রীমন্তী সেনগুপ্ত । এনারা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন বলে জানি । অনেকে যোগাযোগ না করেই, সন্দীপ দত্তর লাইব্রেরি বা অন্য কোথাও থেকে তথ্য সংগ্রহ করে কাজ করেছেন, যেমন রিমা ভট্টাচার্য, উৎপলকুমার মণ্ডল, মধুবন্তী চন্দ, সঞ্চয়িতা ভট্টাচার্য, মহম্মদ ইমতিয়াজ, নন্দিনী ধর, তিতাস দে সরকার, এস মুদগাল, অঙ্কন কাজি, কপিল আব্রাহাম প্রমুখ । উদয়শঙ্কর বর্মা পিএইচডি করেছেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেননি, পুরো আন্দোলন কভার করেননি উনি, উত্তম দাশের সঙ্গে দেখা করলে নথিপত্র পেতেন । ডেবোরা বেকার আমাদের কারোর সঙ্গে বা সন্দীপ দত্তের লাইব্রেরিতে না গিয়ে তারাপদ রায়ের কাছ থেকে তথ্য যোগাড় করেছিলেন আর আবোল-তাবোল লিখেছেন । সুতরাং কে কোথায় গবেষণা করছেন বলা কঠিন। পেঙ্গুইন থেকে মৈত্রেয়ী চৌধুরীর বই ‘দি হাংরিয়ালিসটস’ বেরোবে এই বছর । আগামী বছর রাহুল দাশগুপ্ত আর বৈদ্যনাথ মিশ্রর সম্পাদনায় বেরোবে ‘লিটারেচার অফ দি হাংরিয়ালিস্টস’ । সমীরণ মোদক আমার সম্পাদিত ‘জেব্রা’ পত্রিকা সংকলিত করছেন, ‘হাংরি আন্দোলকারীদের চিঠি’ নামে একটা সংকলন বের করার তোড়জোড় করছেন। অজিত রায় তো এই বিষয়ে লিখে লিখে পাঠকের কাছে বিতর্কটা জিইয়ে রেখেছে ।
জয়িতা: সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা প্রশাখা নিয়ে নানা কাজ করেছো । কোনো বিশেষ বিষয় নিয়ে কাজ করবার ইচ্ছে আছে ?
মলয়: আপাতত একটা উপন্যাস লেখার কথা ভাবছি । বাউল যুবক যুবতী জুটিকে নিয়ে, যারা তারুণ্যে একজন নকশাল আর একজন কংশাল ছিল । কিন্তু তাদের ঘিরে যে চরিত্ররা থাকবে সেই লোকগুলোকে গড়ে তুলতে পারছি না, সুরজিৎ সেনের ‘ফকিরনামা’ বইটা পড়ে আইডিয়াটা এসেছে মাথায়, কিন্তু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নেই বলে এগোইনি । এতেও যুবতীর বয়স যুবকের চেয়ে বেশি। পরস্পরকে মা-বাবা বলে ডাকে । সরসিজ বসু অনুরোধ করেছেন একটা গদ্য তৈরি করতে বর্তমান ভারতের জাতীয়তা, দেশপ্রেম, দাঙ্গা, গরুর মাংস খাওয়া, নিম্নবর্গের মানুষকে কোনঠাসা করার চেষ্টা ইত্যাদি নিয়ে । ‘বসুধৈব জিঙ্গোবাদম’ নিয়ে লিখেছি । ওকে আরেকটা লেখা দিয়েছি, ‘কফিহাউস - অন্তর্ঘাতের পলিমাটি’ নামে, অন্য একটা পত্রিকায় । আশি পেরোতে চললুম, আর বিশেষ কিছু লিখতে ভাল্লাগে না । একঠায় কমপিউটারে বসে থাকতেও তো পারি না ।
জয়িতা :তোমাকে প্রাচীন স্পার্টান বীরের মতো মনে হয় ।এই যে নানা ঘাত প্রতিঘাত নিন্দে মন্দ সব কিছুকে অবজ্ঞাভরে কেবল কাজ করে যাওয়া ,এই জীবনিশক্তির মূলমন্ত্র কি। অনুপ্রেরণাদাতা বা দাত্রী কে ?
মলয় : হলিউড-বলিউডের ফিল্ম দেখে বলছিস বোধহয়, সিলভিস্টার স্ট্যালোনের র্যামবো, থর-এর নায়ক, গ্ল্যাডিয়েটরের নায়ক, নাকি ? কোমরে দড়ি আর হাতে হাতকড়া পরে সাতজন ক্রিমিনালের সঙ্গে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাবার পর, ‘ক্ষুধার্ত গোষ্ঠী’ আমার বিরুদ্ধে রাজসাক্ষী হয়ে কাঠগড়ায় দাঁড়াবার পর, নিন্দে-মন্দ গায়ে লাগে না, লিখেও তো কতো লোকে গালমন্দ করে, বিশেষ করে রাজসাক্ষীদের ছেড়ে যাওয়া ‘ক্ষুধার্ত গোষ্ঠীর’ চেলারা । যখন লেখা আরম্ভ করেছিলুম তখন কুলসুম আপা, নমিতা চক্রবর্তী, বাড়ির চাকর শিউনন্নি, বাবার দোকানের কাজের লোক রামখেলাওন সিং ডাবর ছিল, শেষের দুজন রামচরিতমানস আর রহিম কবির দাদু থেকে কোটেশান ঝেড়ে আমাদের বকুনি দিতো , ব্যাপারগুলো ‘ছোটোলোকের ছোটোবেলায়’ লিখেছি । আমার লেখালিখি নিয়ে আমার স্ত্রী আর ছেলের কোনো আগ্রহ নেই ; মেয়ের আছে, কিন্তু তার হাতে সময় একেবারে নেই, সম্প্রতি সেরিব্রাল স্ট্রোক হয়েছিল । বস্তুত অনু্প্রেরণা বলে সত্যিই কি কিছু হয় ? আমার তো মনে হয় আমি নিজেই নিজের অনুপ্রেরণা, রাস্তায় হাঁটার সময়ে অনুপ্রেরণা মগজে জমতে থাকে।
জয়িতা : তোমার বর্তমান যাপন সম্পর্কে তোমার অনুরাগী পাঠকসমাজকে কিছু জানাও।
মলয়: আমার অনুরাগী পাঠক সত্যিই আছে ? মনে তো হয় না । আমি প্রথমে উঠি, স্ত্রী দেরিতে কেননা ওর রাতে ঘুম হয় না, রাতে উঠে-উঠে হোমিওপ্যাধি ওষুধ খায় । দাঁত ব্রাশ করে ফ্রি হ্যাণ্ড এক্সারসাইজ করি, ফিজিওথেরাপিস্টের শেখানো । এক গেলাস গরমজল খাই যাতে পেট পরিষ্কার হয় । ব্রেকফাস্ট বানাই, ওটস । তারপর ইজিচেয়ারে কিছুক্ষণ বসে টাইমস অফ ইনডিয়া পড়ি । আমার পাড়ায় বাংলা সংবাদপত্র পাওয়া যায় না, এটা গুজরাটি ফাটকাবাজদের এলাকা, একটা ফাইনানশিয়াল টাইমস কিনে দশজন মিলে শেয়ারের ওঠানামা পড়ে । আমি কখনও শেয়ার-ফেয়ার কিনিনি, তাই কোনো উৎসাহ পাই না ওনাদের সঙ্গে গ্যাঁজাতে । হকারকে বললে চারদিনের বাংলা কাগজ তাড়া করে একদিন দিয়ে যায়। নতুন যে লিটল ম্যাগাজিন আগের দিন পেয়েছি সেটা পড়ি । ফিজিওথেরাপির পর চা বানাই, গ্রিন টি । ততক্ষণে স্ত্রী উঠে ওটস ভাগাভাগি করে আর আপেল বা কিউই বা যে ফল হোক কাটে । আমি খেয়ে নিই । স্ত্রী এগারোটায় ব্রেকফাস্ট করে । তারপর বাজার যাই । মাছ-মাংস আর মাসকাবারি চাল-ডাল-তেল-মশলা কেনার থাকলে ফোন করে দিলে দিয়ে যায় । ফিরে এসে এগারোটা নাগাদ কমপিউটারে বসি আর ভাবি । ফেসবুক খুলে, জিমেল খুলে, চোখ বুলিয়ে নিই । তারপর বই আর পত্রিকা পড়ি । একটায় স্নান, খাওয়া, ঘুম । তিনটের সময়ে উঠে টিভিতে ফুটবল খেলা দেখি, ইউরোপের, ভারতের থাকলে ভারতের । সাড়ে চারটের সময়ে বিবিসি । ছয়টা থেকে আটটা কমপিউটারে লেখালিখি আর সিঙ্গল মল্ট খাওয়া, এখন যদিও আর খাই না । তারপর রুটি তরকারি ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমোবার চেষ্টা আর সেই ফাঁকে লেখার সম্পর্কে চিন্তাভাবনা, কেননা ঘুম আসতে দেরি হয় । অনেক সময়ে আমার ছেলের বউ রিয়াধে বসে সুইগি কিংবা ফুড পাণ্ডাকে অর্ডার দিয়ে দেয় আমাদের জন্য, বিরিয়ানি, মিষ্টি দই, নলেন গুড়ের সন্দেশ ইত্যাদির । রাতে ফোন বন্ধ করে দিই, যাতে কেউ ঘুমের দফারফা না করে ।
জয়িতা :আজকাল কবিতাকে দশক হিসেবে ক্যাটিগোরাইজ করা হচ্ছে ; জেলা ও বিষয় ভিত্তিক ক্যাটিগোরাইজ করা হচ্ছে । কতটা প্রাসঙ্গিক বলে তোমার মনে হয় ?
মলয়: এটা এই সময়ের ব্যাপার । সময় আপনা থেকে ঝরিয়ে দেবে যারা প্রাসঙ্গিক নয়, তাদের । প্রতিটি জেলায় কবিদের সংখ্যা তো কম নয় । হয়তো অমন সংকলন বেরোলে জানা যাবে তাদের ওপর জেলা-বিশেষের কথ্যভাষা আর ভূপ্রকৃতির প্রভাব পড়েছে কিনা । আমি নিজে তো জানি না আমি কোন জেলার । পূর্বপুরুষ লক্ষ্মীকান্ত এসেছিলেন যশোর থেকে কলকাতায়, তাঁর বংশধররা বেহালা-বড়িশায় ঘাটি গাড়েন । একজন শরিক ১৭০৩ সালে নদীর এপারে উত্তরপাড়ায় চলে আসেন, আমি তাঁর বংশধর । উত্তরপাড়ার জমিদার বাড়ি ভেঙে আবাসন হয়েছে, আমি আমার শেয়ার বেচে দিয়েছি । তারপর ছিলুম নাকতলায় । নাকতলার ফ্ল্যাট বেচে চলে এসেছি মুম্বাই ; বইপত্র আর আসবাব বিলিয়ে দিয়েছিলুম নাকতলায় । যে বাসা আমি একবার ছেড়েছি, সেখানে আর দ্বিতীয়বার ফিরে যাইনি । আমি একই ঘরে, একই বাড়িতে, একই পাড়ায়, একই শহরে, সারাজীবন কাটাইনি।
জয়িতা :অনুকবিতা সাহিত্যপত্র গুলির নতুন আবিষ্কার । তোমার কি মতামত ? কবিতাকে কি সম্পাদক শব্দসীমায় বেঁধে দিতে পারে? কবি অসহায় বোধ করে অনেক সময়ই ।
মলয় : এটাও কবির সংখ্যাবৃদ্ধির কারণে ঘটছে, অনেককে জায়গা দেয়া যায় অনুকবিতা পত্রিকায় । যে কবি অসহায় বোধ করে তার তো লেখাই উচিত নয় অমন সংকলনে । তবে চীনা আর জাপানি কবিতার প্রভাবে এজরা পাউন্ড ‘ইমেজিজম’ নামে অনুকবিতার আন্দোলন করেছিলেন । In a Station of the Metro নামে ওনার একটা দুই লাইনের কবিতা আছে, যাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অনুকবিতার মান্যতা দেয়া হয়েছে, কবিতাটা শোন
The apparition of these faces in the crowd ;
Petals on a wet, black bough.
জয়িতা : তোমার আন্তর্জাতিক যোগসুত্র বিশ্ব পরিচিতি সম্পর্কে বলো ।এখানকার পাঠকদের জানা দরকার। কোন বিদেশী সাহিত্যিকের সঙ্গে আলাপিত হয়ে মুগ্ধ হয়েছো ? কার বন্ধুত্ব নিবিড় হয়েছে । এখন বিদেশে তোমার রচনা নিয়ে বাংলা প্রেমী বিদেশী ছাত্রছাত্রীরা কতটা সচেতন ?মলয় : হাংরি আন্দোলনের সময়ে হাওয়ার্ড ম্যাককর্ড, ডিক বাকেন, অ্যালেন গিন্সবার্গ, লরেন্স ফেরলিংঘেট্টি, মার্গারেট র্যানডাল, ডেইজি অ্যালান, ক্যারল বার্জ, ডায়না ডি প্রিমা, কার্ল ওয়েসনার, অ্যালান ডি লোচ প্রমুখের সঙ্গে পরিচিত ছিলুম । অ্যারেস্ট করার সময়ে পুলিস ওনাদের চিঠিপত্রের ফাইল নিয়ে চলে গিয়েছিল, আর ফেরত পাইনি । এখন মাঝে-মাঝে প্রিন্ট বা মিডিয়ার সাংবাদিকরা যোগাযোগ করেন, সাক্ষাৎকার নিয়ে যান । স্কটল্যাণ্ডের একটা সংবাদপত্রের পক্ষে নিকি সোবরাইটি নামে এক তরুণী সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন । বিবিসির পক্ষ থেকে দুবার, একবার জো হুইলার আর আরেকবার ডোমিনিক বার্ন সাক্ষাৎকার নিয়ে গেছেন । ড্যানিয়েলা লিমোনেলার কথা আগেই বলেছি, যাঁকে আমার স্ত্রীও ভালোবেসে ফেলেছে, ড্যানিয়েলা বাংলা, হিন্দি, ইংরেজি, জার্মান, ইতালিয়ান বলতে পারে, হাত দিয়ে ভাত খায় আমাদের বাড়ি এলে । আমি আর নিজে থেকে কারোর সঙ্গে যোগাযোগ করি না । জার্মানি থেকে স্হানীয় আর্টিস্ট শিল্পা গুপ্তাকে নিয়ে এসেছিলেন মাইলিওন ; ওনারা একশো কবির প্রদর্শনী করছেন পৃথিবীর বিভিন্ন শহরে, আমার কবিতাটাও অন্তর্ভুক্ত করেছেন । শিল্পা গুপ্তাই আমাকে ছবি আঁকার নানা রকম রঙ, ব্রাশ, পেনিল ইত্যাদি পাঠিয়েছেন, তাই দিয়ে ছবি আঁকছি, দেখেছিস তো? ব্লগে পাঠকের সংখ্যা থেকে মনে হয় নানা দেশ থেকে অনেকেই টোকা মেরেছে কিন্তু তাদের মধ্যে কতোজন পড়েছে বলতে পারব না ।
জয়িতা : কবিতা প্রথম কবে লিখেছ? কেন? সমীরদা লিখতেন বলে?
মলয় : ১৯৫৮ সালে বাবা একটা সুন্দর ডায়েরি দিয়েছিলেন, তাতে লেখা আরম্ভ করি, ইংরেজিতেও লিখতুম । দাদা আমার পরে লেখা আরম্ভ করেছিল । তবে ওই ডায়রি থেকে কবিতা নিয়ে দাদা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে দিতে, উনি কৃত্তিবাস পত্রিকায় ১৯৫৯ সালে প্রকাশ করেছিলেন । সুনীল তখন পাটনার বাড়িতে আসতেন । পরে হাংরি আন্দোলনের জন্য চটে গিয়েছিলেন । ‘যুগশঙ্খ’ পত্রিকার জন্য বাসব রায়কে দেয়া সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন ‘মলয় ইচ্ছে করে আমার আমেরিকাবাসের সুযোগটা নিয়েছিল।”
জয়িতা: হাংরি আন্দোলন সম্পর্কে বিস্তারে না গিয়েও সেই সময়কার কবিতার ডিক্সান কি কোনোভাবে নিকোনার পারার বা বিট আন্দোলনের প্রভাবিত?
মলয় : তখনও আমি ওনাদের কবিতা পড়িনি, নামই শুনিনি । বিদেশি কবি বলতে রোমান্টিক ব্রিটিশ কবিদের পড়েছিলুম । আমার কবিতায় ইমলিতলার মগহি আর ভোজপুরি ডিকশানের প্রভাব থাকতে পারে ; ফণীশ্বরনাথ রেণু, যিনি বাংলা জানতেন, এই কথাটা বলেছিলেন । বিটদের বইপত্র লরেন্স ফেরলিংঘেট্টি পাঠিয়েছিলেন অ্যালেন আমেরিকা ফিরে যাবার পর । আর বিটদের সকলের কবিতা আর গদ্য একই রকম নয়, সকলের রচনাতেই যৌনতা থাকে না । তাছাড়া নিকানর পাররার মতন কবিতা বিটরা লেখেনি । হাংরি আন্দোলনেও আমরা একজন আরেকজনের মতন কবিতা ও গদ্য লিখিনি । ‘ক্ষুধার্ত গোষ্ঠীর’ কবি-লেখকরা সিপিএম করা আরম্ভ করে লেখার ধারা পালটে ফেলেছিলেন । শ্রুতি আন্দোলনে কংক্রিট পোয়েট্রির প্রভাব কিছুটা ছিল বিশেষত পরেশ মণ্ডলের কবিতায় কিন্তু তাঁরাও একই রকমের কবিতা লেখেননি । নিম সাহিত্যেরও সবাই একই রকম লিখতেন না ।
জয়িতা : প্রথম পর্বের কবিতার সঙ্গে এখন যে কবিতাগুলো লিখছ তার শৈলীতে যে পরিবর্তন এসেছে সে সম্পর্কে বলো। প্রথম পর্বের কবিতায় একটা নাড়িয়ে দেওয়া ঝাঁকুনি দেওয়া ব্যাপার ছিলো । তার সিনট্যাক্স ,ডিক্সন স্ট্রাক্চার ছিলো অভূতপূর্ব। দ্বিতীয়পর্বে এসেছ মাঝে অনেকটা সময়,অভিজ্ঞতা ,সংসার ....কবিতা মাঝসমুদ্রের মতো গভীর ও সমাহিত।মিল নেই তবু চেনা যায় এ কবিতা র কবি কে। এই বিষয়ে কিছু বলো ।
মলয় : সে সময়ে কবিতায় টেসটোসটেরন, অ্যাড্রেনালিন থাকত, নিজেদের পত্রিকা আর বুলেটিনে বেরোতো, উদ্দাম নেশা আর যৌনতার ঘনঘটা ছিল । এখন অভিজ্ঞতার আর পড়াশুনার দরুন কবিতায় বদল এসেছে, আপনা থেকেই । যে দেড় দশক লিখিনি, সেই সময়ে প্রচুর পড়াশুনা করেছি । সব বিষয়ে বই পড়তুম। কবি হতে হবে, এই ভেবে তো লেখালিখি করিনি, এখনও করিনা ।
জয়িতা :বাংলায় উত্তরাধুনিক কবিতা কি লেখা হয় ?
মলয় : হয় তো । উত্তরাধুনিক বলতে যে বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয় তা হাল আমলের বেশির ভাগ কবির রচনায় পাওয়া যাবে । অনেক তরুণ-তরুণীর কবিতায় বিস্ময়কর পংক্তি-কারিগরি দেখতে পাই ; বস্তুত ঈর্ষা হয় তাদের কবিতা পড়ে । বারীন ঘোষাল, অলোক বিশ্বাস, প্রণব পাল, ধীমান ভট্টাচার্য প্রমুখের কবিতা পড়লে টের পাবি ।
কিন্তু পোস্টমডার্ন নামের দার্শনিক তত্বের সঙ্গে পোস্টমডার্ন সাহিত্যের সম্পর্কে নেই । পোস্টমডার্ন সাহিত্য মূলত আঙ্গিকের প্রাধান্যের ব্যাপার । ঠিক যেমন আধুনিক কবিতার সঙ্গে মডার্নিটির দর্শনের সম্পর্ক নেই ।
জয়িতা :তোমার পছন্দের কবি কারা (আন্তর্জাতিক ও বাংলা সাহিত্যে)
মলয় : বাংলায় বিনয়, ফালগুনী, কেদার ভাদুড়ি, জহর সেনমজুমদার, প্রদীপ চৌধুরীর চর্মরোগ, মণীভূষণ, যশোধরা, মিতুল, হেলাল হাফিজ, রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ প্রমুখ । সব নাম এক্ষুনি মনে পড়ছে না, আরও কিছু নাম বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে বলে থাকব, প্রবন্ধে লিখে থাকব । বিদেশি পল সেলান, সিলভিয়া প্লাথ, মায়া অ্যাঞ্জেলু, জন অ্যাশবেরি, আমিরি বারাকা, ইভস বনেফয়, জ্যাক দুপাঁ প্রমুখ । আর বলছিনা, তুই প্রভাব খুঁজবি ।
জয়িতা : হাংরি আন্দোলন আর তোমাকে নিয়ে বাংলা আর ইংরেজিতে গবেষণা হচ্ছে । এতে তোমার গর্ববোধ হয় ? নাকি যা চাইছিলে তা পেয়ে গেছো বলে মনে হয় ?
মলয় : আমার কিছুই হয় না । যারা আক্রমণ করতেন তাঁদের বিরক্তি হয় বলে মনে হয় । কিছুদিন আগে প্রতিদিন পত্রিকায় অরুণেশ আর আমার বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল কমল চক্রবর্তী, হাংরি আন্দোলনকারীদের প্রশ্রয় দিলেও তারা ওর বেদনার কারণ হয়েছে । সত্যি কথা বলতে কি আমার আর অরুণেশের কাব্যগ্রন্হ অত্যন্ত বাজে নিউজপ্রিন্টে ছেপেছিল, কভারও ফালতু করেছিল, তাই আমাদের মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল, যখন কিনা ওদের নিজেদের বইগুলোর প্রোডাকশান দারুণ হয়েছিল । যাকগে, আর তো নিজের বইপত্তর রাখি না, সব বিলিয়ে দিয়েছি, এখনই মুম্বাইতে এসে এখানকার কবি-লেখকদের দিয়ে দিই ।
জয়িতা : উচ্চারণ না অক্ষর কোনটা মানা উচিত ছন্দের ক্ষেত্রে।
মলয় : আমি তো মাত্রা গুণে লিখি না । উচ্চরণ অনুযায়ী লিখি ।
জয়িতা: তুমি বিদেশী কবিতা পড়ে আপডেটেড হতে বলো কিন্তু কবিতায় ষোলোয়ানা বাঙালি সেন্টিমেন্ট তার নিজস্ব ডিক্সনেরও কি প্রয়োজন নেই।সেই রূপান্তর কে অনুসরণ বা নকল বলা যায়কি? যেটা জীবনানন্দ বা অনেককেই শুনতে হয়েছে ।
মলয় : বিভিন্ন ভাষার সাহিত্য পড়লে জানা যায় যে পৃথিবীর ভাষা সামগ্রিকভাবে কোনদিকে যাচ্ছে । নকল করার দরকার হয় না ।
জয়িতা: কবিতা ও গল্পে প্রান্তিক ভাষার সংলাপ ব্যবহার তোমার সময় বেশি লোক করেনি।কী ভাবনা কাজ করেছে এর পেছনে।
মলয় : সেসময়ে কলকাতাকেন্দ্রিক লেখকরা লিখতেন । পরে মফসসলের লেখকরা লেখা আরম্ভ করলে প্রান্তিক ভাষার প্রবেশ ঘটে । সুবিমল বসাক ১৯৬৫ থেকেই প্রান্তিক ভাষাকে গুরুত্ব দিয়ে আসছেন । রবীন্দ্র গুহ আর অরুণেশ ঘোষও প্রান্তিক ভাষাকে ওনাদের গল্পে এনেছেন ।
জয়িতা : সাহিত্যে যৌনতা এসেছে শিল্প হয়ে কিন্তু একদম নগ্ন ও আপোষহীন। পাঠক চমকে উঠেছে। যা বিছানায় যা জৈবিক তাকে সৃজনেও ঠিক সেইভাবেই আনা প্রয়োজন এটা তোমরাই করেছ। আমি তোমার কথাই বলবো। সাহিত্যে যৌনতা উন্মুক্ত ও আলোকিত হয়েছে নানাভাবে কখনো চরিত্রের মধ্যে কখনো কবিতা বা আত্মকথায়, বিশেষ করে 'অরূপ তোমার এঁটোকাঁটা' উপন্যাসে । সে ব্যাপারে কিছু বলো।
মলয় : যৌনতা অনেককাল থেকেই ছিল সংস্কৃত আর বাংলা সাহিত্যে । ইভানজেলিকাল পাদরিরা স্কুল-কলেজের সিলেবাসে মাথা গলানোর পর আর তাদের শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ গড়ে ওঠার পর যৌনতা নিয়ে দোনামোনা আরম্ভ হয়েছিল । তারপর ব্রাহ্মদের প্রভাব, বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের । সাহিত্য যখন মধ্যবিত্তের আর উচ্চবর্ণের আওতা থেকে বেরোলো তখন যৌনতা নিজের স্বাভাবিক চরিত্র পেলো ।
জয়িতা : তুমি সলিলাদির সঙ্গে পরিচয়ের পরের দিনই বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলে আর উনি তক্ষুনি রাজি হয়ে গিয়েছিলেন, সলিলাদের অভিভাবকরা ইতস্তত করছিলেন বলে তোমরা নাকি পালিয়ে যাবার টিকিট কেটে ফেলেছিলে । তার পর এক সপ্তাহেই বিয়ে সেরে বউকে নিয়ে পাটনায় ফিরলে । তোমার অবাক লাগেনি ওনার তখনই রাজি হয়ে যাওয়ায় ? তোমার বাবা-মা কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া জানাননি ?
মলয় : না, সলিলা ছিল হকি খেলোয়াড়, ডিসিশন নিয়েছিল স্পোর্টসগার্লের মতনই । ওর বন্ধু সুলোচনা নাইডু ওকে হিন্দি ম্যাগাজিনে প্রকাশিত আমার ফোটো আর সংবাদ পড়িয়েছিল । তাছাড়া ওর বাবা-মা ছিলেন না । মামার বাড়ির বাঁধন ছিঁড়ে চলে যেতে চাইছিল । মামারা দোনামোনা করেছিলেন সলিলার মাইনে ওনাদের সংসারে কাজে দিতো। আমরা তো দুজনে নাগপুর ছেড়ে চুপচাপ পাটনায় চলে যাবার টিকিট কেটে ফেলেছিলুম, কিন্তু তা করলে ওর অফিস থেকে ছুটি নিতে হতো, বিয়ের প্রমাণ না দিলে পরে ট্রান্সফারের সমস্যা হতো, ও চাকরি ছাড়তে চায়নি ; তুই তো স্কুলে পড়াস, মেয়েদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়াটা কতো জরুরি তা জানিস । সলিলার মামাতো বোনের বিয়ে ঠিক হয়েছিল দুদিন পরেই । ওরা বিয়ে করে উঠল আর আমরা সেই পিঁড়িতে বসে পড়লুম । আমি আমার বিয়ে নিয়ে একটা লেখা তৈরি করছি, অজিত বই করে বের করবে । বাবা-মা তো বউ পেয়ে যাকে বলে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিলেন । মা বলেছিলেন সিঁদুর পরিয়ে বাড়ি আনলেই হবে, আচার-টাচারের দরকার নেই । সত্যই বিয়ের আচার বলতে যা বোঝায় তা সম্ভব হয়নি , নাগপুরেও নয়। পাটনায় ফিরে তো কিছুই হয়নি ।
জয়িতা: বিয়ে করে তুমি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের চাকরি ছেড়ে চলে গেলে এআরডিসি লখনউ, সেখান থেকে মুম্বাই নাবার্ডে, তারপর কলকাতার নাবার্ডে। এতো পরে কলকাতায় এসে তোমার কি মনে হলো যে হাংরি আন্দোলনের দিনগুলো আর নেই ।
মলয় : লখনউ যাবার পরেই আমি ভারতের গ্রামসমাজের সঙ্গে পরিচিত হলুম । তার আগে চাষবাস, ফসল, কলকারখানা, তাঁত, ছুতোরের, কামারের, হাতের কাজের মজুরের ব্যাপারে কিছুই জানতুম না । কতোরকমের ধান, গম, জোয়ার, বাজরা, গোরু, ছাগল, শুয়োর, উট হয় জানতুম না ; তাদের ব্রিডিং সম্পর্কেও জানতুম না । সারা ভারত ঘুরেছি অফিসের টাকায়, পশুগুলোও এক এক জায়গার এক এক রকম । শেষদিকে আমি সলিলাকেও সঙ্গে নিয়ে যেতুম, যখন ও চাকরি ছেড়ে দিলো, যাতে পরিবারগুলোর বাড়ির ভেতরের অবস্হা জানতে পারে । সব অভিজ্ঞতা উপন্যাস আর প্রবন্ধ লেখায় কাজে লাগিয়েছি । হ্যাঁ, যখন ফিরলুম তখন পশ্চিমবাংলার সমাজ নানা দিক থেকে পালটে গিয়েছিল । আমি ‘আরেকবার ক্ষুধিত পাষাণ’ নামে একটা প্যাশটিশ লিখেছি, সাঁইবাড়ির হত্যাকাণ্ড নিয়ে । ঝুমা চট্টোপাধ্যায় ভাঙা আর বন্ধ সাঁইবাড়ির প্রচুর ফোটো তুলে পাঠিয়েছিলেন, সেগুলো দেখে আইডিয়াটা হলো। অনেকে লেখে আমি সরকারি চাকরি করতুম ; ধারণাটা ভুল । সরকারি চাকরি করলে ফাইনান্স কমিশন যখন সরকারি কর্মীদের মাইনে আর পেনশন বাড়িয়ে দেয়, তখন আমার বাড়ে না, সরকার কর্মী নই বলে । পেনশন সেই ১৯৯৭ সালে যা ছিল সেখানেই আটকে আছে ।
জয়িতা : তুমি বাংলা সিরিয়াল দ্যাখো ? ফিল্ম দ্যাখো ?
মলয় : সলিলা কোনো-কোনো বাংলা সিরিয়াল দেখে, পছন্দ না হলে অন্য সিরিয়ালে চলে যায় । আমিও খেতে বসে দেখি যেগুলো সেসময়ে সলিলা দেখে । আমার মনে হয় যারা বাংলায় কথা বলে তাদের সঙ্গে আমাদের দুজনের যোগাযোগ বাংলা সিরিয়ালের মাধ্যমে । এখানে সারাদিনে বাংলায় কথা বলা আর শোনার সুযোগ নেই। ইউ টিউবেও বাংলা কবিতাপাঠ বা শর্টফিল্ম দেখি । কিন্তু আমার কমপিউটারটা এতো পুরোনো যে প্রায় কিছুই শোনা যায় না । ইনবক্সে গাদাগাদা ভিডিও পাঠায় অনেকে, কিছুই শোনা হয়ে ওঠে না । কমপিউটারের সামনে ঝুঁজে বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারি না । সিনেমা হলে প্রায় চল্লিশ বছর যাইনি ।
জয়িতা : তুমি কোন রাশির জাতক ?
মলয় : সিংহ রাশি । দাদা মীন রাশি । বাবা বলতেন যে দাদা মীন রাশি বলে ফিশারিজ বিভাগে ঢুকে পুকুর, নদী, সমুদ্রে ঘুরে বেড়ায় আর আমি সিংহ রাশি বলে চরে বেড়াই ।
 অজিত রায় | 27.58.255.50 | ১০ আগস্ট ২০২১ ১৯:৩৬734851
অজিত রায় | 27.58.255.50 | ১০ আগস্ট ২০২১ ১৯:৩৬734851অজিত রায় : মলয় রায়চৌধুরীর সাহিত্যপ্রতিভা
মলয় রায়চোধুরীর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় পঁয়ত্রিশ বছর আগে। সামান্য অভূয়িষ্ট পড়াশোনা থেকে ক্ষুধিত প্রজন্মের কবি ও কবিতা নিয়ে একটা আচাভূয়া লেখা লিখেছিলাম ১৯৮২ সনে, এক মফস্বলী কাগজে, সেই তখন। সেদিনের সেই সব্রীড় আত্মপ্রতর্ক থেকে প্ররোচিত হই মলয়-সিসৃক্ষার কলিন অধ্যয়নে। ততদিনে, তার বিশ বছর আগেই হাংরি আন্দোলনের অন্যতম এই স্রষ্টার নখদন্ত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের শরীরে কিছু পিরেনিয়্যাল আঁচড় কেটে ধাবাড় মেরে গেছিল। ১৯৬১ থেকে ১৯৬৫-কেই বলা যায় হাংরি আন্দোলনের সবচেয়ে উত্তেজক আর ঘটনাবহুল অস্তিত্বকাল।
এহেন বিশাল ব্যবধানে, এই প্রেক্ষিতে কুড়ি-বাইশ বছর আগে বাংলা সাহিত্যের প্রচলিত সংস্কারের বিরুদ্ধে, তার পচা ভিত্তিকে উৎখাত করার একান্ত অভীপ্সায় দুর্বিনীত আসব যিনি করেছিলেন, সেই মলয় রায়চোধুরী বিশ বছর বাদে লেখালেখির জগতে প্রত্যাবর্তন করতে চাইলে তাঁর কাছে প্রধান সমস্যাটা কী হতে পারে? এমনিতে পঞ্চাশের কবিরা যাঁরা হাংরি আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন, আন্দোলন ফুরিয়ে যাবার পর নিজেদের চরিত্র মোতাবিক লিখে আসছিলেন। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের এতোলবেতোল জীবন শুরু হয়ে যায় আর তিনি রূপচাঁদ পক্ষী হয়ে যান, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় একটা নির্দিষ্ট গদ্যে রেওয়াজ করতে করতে নিজস্ব অসাধারণ শৈলীতে থিতু হন। বিদেশ থেকে ফিরে উৎপলকুমার বসুও কাব্যচর্চার নবাঞ্চল আবিষ্কার করেন। শক্তি ও সন্দীপনকে একটি বুলেটিনে আক্রমণ করে বিনয় মজুমদার আগেই বিদায় নিয়ে চলে যান। ষাটের কবি-লেখক হিশেবে অশোক চট্টোপাধ্যায়, সুভাষ ঘোষ, বাসুদেব দাশগুপ্ত, সুবো আচার্য, দেবী রায়, সুবিমল বসাক, শৈলেশ্বর ঘোষ, অরনি বসু, শম্ভু রক্ষিত, প্রদীপ চোধুরী, রবিউল, আপ্পা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের লেখালেখি থেমে থাকেনি এবং দেখা গেছে বয়স, অভিজ্ঞতা ও সিরিয়াসনেসের দরুন এঁদের কেউ কেউ খুঁজে পেয়েছেন নিজস্ব ভাষাবিন্যাস, ফর্ম, চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গিতে একজন আলাদা হয়ে উঠেছেন অন্যজনের থেকে। প্রত্যেককে ঘিরে অল্পসংখ্যক প্রশংসক ও গবেষক গড়ে উঠেছে।
মলয়ের কেসটা এঁদের চেয়ে আলাদা। এবং আপাত জটিল। বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির পীঠস্থান হিশেবে বিজ্ঞাপিত কলকাতা-শান্তিনিকেতনের ধুলো মলয় নিজের পায়ের চেটোয় লাগতে দেননি । কলকাতার একটা পুশিদা ক্লোমযন্ত্র আছে যা বামুন আর চাঁড়ালকে শুঁকে চিনতে পারে। মলয় যেমন কলকাতার সংস্কৃতিকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন, কলকাতা মলয়কে নিজের দাঁত দেখিয়ে দিয়েছিল, পুলিশ-আদালত-জেলজরিমানা ঘানিতে ঘুরিয়েছিল।
কলকাতা আর তাঁর ‘ক্ষুধার্ত’ বন্ধুবান্ধব তাঁকে বুঝিয়ে দিয়েছিল, তুমি আমাদের কেউ নও। তুমি একটা কৃষ্টিদোগলা। তোমার কলমে ইমলিতলার নিম্নবিত্ত রক্ত। তোমার টেক্সট আলাদা। আলাদা থিসরাস। তফাৎ হটো তুমি। বিরক্ত, অপমানিত মলয় কলকাতার সঙ্গে সমস্ত শরোকার ছিন্ন করেন । কফিহাউসে তিনি কোনো টেবিলে গিয়ে বসলে সবাই উঠে চলে যেতেন । মুচলেকা ও রাজসাক্ষী হবার পর ‘ক্ষুধার্ত’ বন্ধুরাও তাঁকে এড়িয়ে চলতেন । ২৭ জুলাই ১৯৬৭, মানে, হাইকোর্টের রায়ে বেকসুর খালাস পাওয়ার পরদিন থেকে মলয় কবিতা লেখা ছেড়ে দেন। সবায়ের সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন করেন, আর ক্রমশ নিজেকে অসীম একাকীত্বে ঘিরে ফেলেন। প্রশাসন ও প্রতিষ্ঠানের দুর্গদ্বার থেকে অপরিগৃহীত হয়ে লেখার জগৎ থেকে একান্তে অপসৃত হয়ে স্বরচিত নির্জনতার এক সুচারু এরিনায় নিজেকে বন্দী রেখে, রাইটার্স ব্লকের অখল জ্বালা ভোগ করা ---- হাংরিদের মধ্যে এটা একমাত্র মলয়ের ক্ষেত্রেই ঘটেছে।
আত্মবিবাসনের সেই বিবিক্ত দিনে, ১৯৬৮-র ডিসেম্বরে মধ্যপ্রদেশের রাজ্যস্তরীয় হকি খেলোয়াড় ও অনাথ যুবতী শলিলা মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে উদ্বাহ সাময়িক স্বস্তি ফিরিয়ে আনে তাঁর জীবনে। জীবন নামক ভেলকিবাজ বারে-বারে মানুষকে ষাঁড়ের গোবর করে। চটকায়। ঘুঁটে বানিয়ে শুকোতে দেয়। আবার, পেড়েও আনে। জীবন লিখেওছে এমন এক ফিচেল কেলিকিন, যে কবিতা বোঝে না, সাহিত্য বোঝে না । মন বোঝে না। আদর্শ বোঝে না। আলোপিছল প্রতিষ্ঠানের মসৃণ করিডর দিয়ে হাঁটিয়ে সটান তুলে দেয় আরাম, স্বাচ্ছন্দ্য আর কর্তৃত্বের সুনিপুণ এলিভেটারে। অর্থাৎ 'একদা আপোষহীন' পরে 'অংশভাক' এই ঐতিহাসিক গল্পের পুনরাবৃত্তি মলয়ের জীবনে ঘটাল সেই নর্মদ। এই ট্রাজেডির জন্যে আমরা ইতিহাস আর সময়কে বাদ দিয়ে বরাবর ব্যক্তিকে দায়ী করি, তাকে ব্যক্তির ট্রাজেডি হিশেবে চিহ্নিত করে সৌমনস্য উপভোগ করি, সে আমাদের প্রবলেম। একাকীত্ব ছিল মলয়ের প্রতিশোধ ।
কিন্তু ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি এক অনৈতিহাসিক তত্ত্ব। এ-খবর সত্যি যে বিবাহোত্তর প্রবাসে কিছুদিনের জন্যে মধ্যবিত্ত সংসারী হয়ে উঠেছিলেন মলয়, বিদেশি মদ, বিদেশি সিগারেট ও তরুণ-তরুণী অফিসারদের মধ্যমণি হিসাবে। সৃজন, সাহিত্য, লেখনকর্ম ইত্যাদি থেকে আরও দূরে সরে থাকবার মতো সরঞ্জাম তখন মজুত। মলয় নিজেকে গড়ে তুললেন ইংরেজি সাহিত্য ও দর্শনের বই পড়ে, ভারতের গ্রামাঞ্চলে অবিরাম ট্যুর করে । মৎসরী বন্ধুরা হয়তো এই ভেবে কিঞ্চিৎ আরামও উপভোগ করেছিলেন যে গার্হস্থ্য দায়িত্ব নির্বাহ করা ছাড়া মলয় 'আর কিছুই করছেন না'। কিন্তু তাঁদের গুড়ে বালি নিক্ষেপ করে আশির দশকের গোড়ার দিকে বারদিগর লেখালেখির জগতে তুমুল বেগে ফিরে এলেন কবি-ঔপন্যাসিক ও তাত্বিক মলয় রায়চোধুরী। কলকাতা থেকে লখনউ গিয়ে তাঁর দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিলেন মহাদিগন্ত প্রকাশনীর উত্তম দাশ ও তাঁর স্ত্রী মালবিকা ।
প্রত্যাবর্তিত মলয়ের মধ্যে অনেক মাল, অনেক ময়ুজ, অনেক অস্ত্রশস্ত্র। মানে, দারুণ-একটা রায়বেঁশে, হৈ হল্লা, তারপর নর্তকের আর কোমর-তোমার রইল না, মলয়ের কেসটা সের'ম নয়। তিনি যে হাত-পা ছুঁড়েছিলেন, বেশ-কিছু জ্যামিতিক পারফরম্যান্স দেখিয়েছিলেন ----- বিশ বছর বাদেও দেখছি, সেই কোরিওগ্রাফিটা থেকে গেছে। দেখেশুনে তো মনেই হচ্ছিল গুঁতো দেবার তালেই ছিলেন যেন। আর, গুঁতোবার আগে যেমন মাথা নিচু করে কয়েক পা পিছিয়ে যায় অগ্নিবাহন, তেমনি করে হয়তো-বা আবার করে অঙ্গহার দেখাবেন বলে খানিক জিরিয়ে নিচ্ছিলেন তিনি। কিম্বা, লেখা ছাপানো বন্ধ রেখে পরখ করে নিচ্ছিলেন তিনি টিঁকে আছেন, না উবে গেছেন।
১৯৮০-৮২ নাগাদ, বিশ বছর বাদে ফিরে-আসা সেই হৈচৈ-হীন নিরুত্তেজ উদ্দান্ত-যমিত শান্ত অব্যস্ত নিরুদ্বেগ ঠাণ্ডামাথা মলয় রায়চোধুরীর মধ্যে সে দিনের সেই উত্তপ্ত অস্থির আন্দোলিত প্রবহস্রোতের মাঝে অবগাহনরত মলয় রায়চোধুরীকে খুঁজতে যাওয়া গোঁয়ার্তুমি মাত্র। তবে, বুকের মধ্যে ঢেউয়ের সেই দাপানিটা আর নেই বটে, কিন্তু পানখ সাপের ফণাটা এখনও উদ্যত। সেই কর্কশ আর গতলজ্জ ভাষা, নিলাজ শব্দানুক্ৰমণের ফলাটা এখনো তেমনি পিশুন। আর তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নতুন করে বেড়ে-ওঠা অদম্য উৎসাহ, জেদ আর স্বশিক্ষিত সামর্থ্য। যেন পুরনো দখলতি হাসিল করতেই তাঁর ফিরে আসা। তবে হাংরি আন্দোলনকারী হিসাবে নয় ।
মলয়ের প্রাইম কনসার্ন হলো কবিতা। কবিতার মধ্যেই যা-কিছু দেখা ও দেখানো। ছয়ের দশকের মলয়ের চেয়ে অনেক বেশি লিখেছেন আটের দশকের প্রত্যাবর্তিত মলয়, দেখালেন তাঁর ‘মেধার বাতানুকূল ঘুঙুর’ কাব্যগ্রন্হে। প্রকাশ কর্মকারের ড্রইং এবং তাঁর কবিতার যুগলবন্ধন বুলেটিনে । পূর্বাপরের সঙ্গে স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় একটা সীমারেখা তিনি গড়ে ফেলেছেন অনেক দিন আগেই। কী কবিতায়, কী গদ্যে পুনরুত্থিত মলয় খুব সচেতনভাবে নিজের একটা জায়গা বানিয়ে নিয়েছেন, এটা অবম বা ঊন কথা নয়। বাংলা সাহিত্যে প্রথা ভেঙে যেখানে কিছুই হয় না, মলয় রায়চোধুরী সেখানে একটা তাক-লাগানো মিশাল। পুনরুত্থিত মলয় গদ্যকার হিশেবেও অভিনিবেশযোগ্য। একটা আপাতজটিল, বর্ণময়, গতিশীল, বহুস্বর আর বহুরৈখিক গদ্যের কারিগর তিনি। তাঁর বাল্যস্মৃতি ‘ছোটোলোকের ছোটোবেলা’ সম্পূর্ণ ভিন্ন এক কৈশোরজ গদ্যবিন্যাসে রচিত, একাধিক সংস্করণ হয়েছে । পরবর্তী পর্ব ‘ছোটোলোকের যুববেলা’ও তাই । এবং শেষ পর্ব ‘ছোটোলোকের জীবন’ তো এক ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছে তাঁর গদ্যে ।
হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের সময়ে লেখা বিভিন্ন ইস্তেহার, প্রবন্ধ, পরবর্তী বা আটের দশক থেকে বিভিন্ন পত্রপত্রিকার জন্য লেখা হাংরি বিষয়ক আলোচনা, স্মৃতিচারনা, সাহিত্যও সাহিত্যিক বিষয়ক নিবন্ধ, তাঁর 'হাংরি কিংবদন্তী' (১৯৯৪) এবং ‘হাওয়া ৪৯’ প্রকাশনীর 'পোস্টমর্ডানিজম' (১৯৯৫) এবং ‘হাওয়া৪৯’ ত্রৈমাসিক পত্রিকায় বাহন হয়েছে এই আকর্ষণীয় ও মূল্যবান গদ্য। লিখেছেন উত্তরঔপনিবেশিকতা, নারীবাদ, অপরত্ব, সংকরায়ণ, জটিলতা ইত্যাদি নিয়ে ।
অন্যদিকে আর একটি গদ্য আছে তাঁর, যা বিভিন্ন নিরীক্ষার পর্যায়ে, যাতে অনিবার নতুন আর আপাত-জটিল শব্দের তোড়, তাকে আশ্রয় করে মলয় তাঁর এখনকার মৌলিক গল্প-উপন্যাসগুলি লিখছেন। দারুন মডার্ন প্রোজ। দারুণ-দারুণ সব কৌণিকময়তা, বহুস্বর, যে-মুহূর্তে ক্লিক করেন, মলয় আমাদের কাছে এ-সময়ের একজন মেজর গদ্যকার হিশেবে ফুটে ওঠেন। কিন্তু, এখানে তিনি শর্ট ডিস্টান্স রানার। বেশিক্ষণ নাগাড়ে ছুটতে পারেন না। এক-একটা প্যারাগ্রাফের দারুণ স্পিড, কিন্তু প্যারা ফুরোতেই যে দমও ফুরিয়ে আসে। মলয়ের বেশির ভাগ গল্প-উপন্যাস এই শ্রেণীর গদ্যে লেখা। যে, কারণে, শুধুমাত্র গদ্যের এই রেসের কারণেই তাঁর 'নামগন্ধ' বাদে অন্য কোনো উপন্যাস আমায় টানেনি। এটা আমার ব্যক্তিগত গদ্যকার হবার কুফলের দরুনও হতে পারে।
কবিতার মতো গদ্যেও মলয় খুব ইমেজ ও শব্দ-সচেতন। কোনো-কোনো রচনায় যেন অতিরিক্ত সচেতন। প্রায় প্রত্যেকটা শব্দেই অনেক বেশি করে কলেজা-রক্ত, কিন্তু নুনের পরিমাণ একটু বেশি। শব্দ-ব্যাপারে মলয়ের ঢালাইঘরে অনবরত হিট ট্রিটমেন্ট। দারুণ বর্ণনানির্ভর মেদবিহীন গতিশীল গদ্যের তিনি প্রাকৃত-ভাণ্ডার। কিন্তু যেইমাত্র সচেতন হয়ে ওঠেন যে তিনি গল্প বা উপন্যাস লিখছেন, সেইমাত্র একরাশ আগুন-হলকা তাঁর হাত দিয়ে চাঁদির চন্দোত্তরি করে ফেলেন। ফলত স্ক্র্যাপ আয়রন আর স্টেইনলেস হয় না। ক্র্যাক হয়ে যায়। তিনি ভালোভাবেই জানেন, ধরো তক্তা মারো পেরেক গোছের লেখক তিনি নন। তবু মারা তিনি থামাতে পারেন না। যার ফলে পেরেকের পর পেরেক ভোঁতা হয়ে-হয়ে বেঁকে বেঁকে যায়। এর ফলে কী হয়, কোনও কোনও অনুচ্ছেদ খুব দারুণ লাগলেও খুব কনট্রাইভড, গদ্য বানাবার দাগগুলো চোখে পড়ে যায়। এটাকে মলয়-গদ্যের দুর্বলতা বলুন, বা বৈশিষ্ট্য।
এই অবক্ষ্যমান গদ্যেই আমি মলয়ের 'দাফন শিল্প' পড়ি ১৯৮৪সালে, 'এবং' পত্রিকায়, যা পরে তাঁর প্রথম গল্পসংগ্ৰহ 'ভেন্নগল্প'-র অন্যতম ভূমিকা হিশেবে পুনর্মুদ্রিত। আবার সেই একই গদ্যে, সামান্য আলগা-ভাবে লেখা তাঁর প্রথম নভেলা 'ঘোঘ' পড়ি ১৯৯২ সনে এবং সেই গদ্যের উত্তরণ দেখি তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'ডুবজলে যেটুকু প্রশ্বাসে' (১৯৯১-৯৩ সালে লেখা, এবং ১৯৯৪-এ প্রকাশিত)। তাঁর পরবর্তী উপন্যাস 'জলাঞ্জলি'ও এই গদ্যে লেখা। এমনকি আমার-পড়া তাঁর সর্বশেষ উপন্যাস 'নামগন্ধ'ও সেই একই গদ্যে লেখা। ভেন্নগল্পের এক ডজন ছোটগল্প আর এই তিনটি উপন্যাস পড়ে বুঝেছি, তাত্ত্বিক মলয় আর লেখক মলয়ের মধ্যে একটা দারুণ প্রত্যাসত্তি রয়েছে। কিছু সর্ব-অস্তিত্বময় বর্তিষ্ণু চরিত্রকে ঘিরে লেখকের নিজস্ব ট্যুরজীবন থেকে হাসিল অভিজ্ঞতা, নানা অন্তর্দেশীয় চেতনা আর আচার-আচরণের সঙ্গে সমকালীন রাজনীতির জটিল প্রভাব, তত্ত্ব ও তথ্যের প্রাচুর্যের সঙ্গে বোধ, অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধির বিচিত্র জটিলতার এক-একটি ছবি ফুটে উঠেছে এইসব গল্প-উপন্যাসে।
কলকাতার পাতি কাগজগুলোতে বিশেষত 'ডুবজলে'র উচ্চকিত প্রশংসা পড়ে এটা ভাবা ঠিক হবে না যে বাঙালি পাঠকরা তাঁদের প্রোডরম্যান ফেজ কাটিয়ে উঠেছেন। আসলে আলোচক-পাঠকদের একটা গ্রূপ যে আক্রান্ত হয়েছিলেন, তার মূলে বাংলা সাহিত্যের অনেক অচ্ছুৎ-অব্যবহৃত শব্দ আর ছবি একটা বিল্টি কেটে পাঠানো হয় সেই প্রথম। সতীনাথ ভাদুড়ী, প্রফুল্ল রায়, রবীন্দ্র গুহ, সুবিমল বসাককে মনে রেখেও বলা যায়, আবহমান বাংলা আখ্যান-সাহিত্যের ট্রাডিশনে যা আগে কখনো এভাবে খাপ খায়নি। মোটামুটি সবই এসেছে মগহি-ভোজপুরি বলয় থেকে। বিশেষ করে বিহারের দেশোয়ালি আর সড়কছাপ জং-মরচে লাগা শব্দগুলোকে সামান্য ঝেড়েঝুড়ে তোলা হয়েছে এই ফিকশানে। ঐ ষাট-সত্তর দশক থেকেই বিহারি-ঝাড়খন্ডি বঙ্গকৃষ্টি দারুণ-দারুণ ঝাপটা মেরে বাংলা সাহিত্যের ঘাটে এসে লাগতে শুরু করেছিল। একটা সফল ঝাপটা ছিল ন'য়ের দশকের 'ডুবজলে'। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে লেখা, বিহারের আর্থ-সমাজ-সংস্কৃতি-রাজনীতির এমন ভিতর-বার গুলিয়ে ফেলা ফিকশান আর কোথাওটি পাননি কলকাতার কূপব্যাঙ আলোচক-পাঠকরা। আর তাতেই তাঁরা দারুণ অমায়িক হোস্টেস হয়ে পড়েছিলেন 'ডুবজলে যেটুকু প্রশ্বাস’-এর। কিন্তু, এটা, মলয়ও জানতেন, রানওয়ে মাত্র--- তিনি উড়ান দেখাবেন পরবর্তীতে। ‘ডুবজলে-র পরে লিখলেন ‘জলাঞ্জলি’। সেই উড়ান-ই হলো মলয়-ট্রিলজির পর্দাফাঁস উপন্যাস 'নামগন্ধ'। এই ট্রিলজিতে মলয় আরও দুটি উপন্যাস সংযোজিত করেছেন যা আমার পড়া হয়ে ওঠেনি, ‘ঔরস’ এবং ‘প্রাকার পরিখা’ ।
মলয় জনান্তিকে বলেছেন, ‘নামগন্ধ’ উপন্যাস পশ্চিমবঙ্গের কোনো সম্পাদক ছাপতে সাহস পাননি, যে কারণে ঢাকার লালমাটিয়া থেকে ‘মীজানুর রহমানের ত্রৈমাসিক পত্রিকায়’ বেরিয়েছিল আগে। পরে ‘হাওয়া ৪৯’ পত্রিকায় এবং গ্রন্হাকারে বেরোয়। গোড়াতেই ফাঁস হয়ে গেল ‘নামগন্ধে’ কী মাল তিনি দিয়েছেন এবং যা অবধার্য হয়ে উঠেছে এসময়ে, মলয়ের পাঠকৃতি সেই আধুনিক ঝোঁকে স্বতঃউৎসারিত। স্বীয় আয় করা দৃঠি ও অভিজ্ঞতাকে ছিঁড়ে পাঠবস্তুর টুকরো পাত্রে স্বত্বহীনভাবে বিলিয়ে দিচ্ছেন বহুরৈখিক-বহুস্বরিক আয়ামে। তাঁর অন্যান্য রচনার মতো এ উপন্যাসও দামাল ঝাপটা মারে ঝাদানভ-প্লেখানভদের বাঙালি ভাবশিষ্যদের এতদিনকার নির্বিঘ্নে মেলে রাখা অরজ্ঞানডির ভুলভুলইয়াপনায়। আলুচাষিদের দুর্দশার জগতে ‘নামগন্ধে’র কাহিনী পরিণাহটি ন্যূন, বক্তব্যেই মূলত মাটাম ধার্য করেছেন মলয়। তিনি সঠিক কষে ফেলেছেন যে বর্তমান কালখণ্ডে দেশভাগোত্তর ভারতবর্ষীয় হিন্দু-বাঙালির তথাকথিত সংস্কৃতি মূলত ক্ষমতাকেন্দ্রের ও তার চারপাশের সংস্কৃতি। মানে, ঐ কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী হাওড়া-হুগলি-চব্বিশ পরগণার সংস্কৃতি। সুতরাং গুনসুঁচ নিয়ে ধেয়েছেন ওই ক্ষমতাকেন্দ্রটিকে বেঁধবার জন্য।
মলয়ের ‘অরূপ তোমার এঁটোকাঁটা’ ভাষার আরেকটি নবাঞ্চল । যৌনতার বিভিন্ন আঙ্গিকের পটভূমিতে তিনটি চরিত্র বাংলাভাষাকে কীভাবে পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে, তা তুলে ধরেছেন মলয় । একইভাবে, তিনি আমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন যে তিনি ডিটেকটিভ উপন্যাস লিখলে তা বাংলা উপন্যাসের বাজারি ট্র্যাডিশানকে কেমন ভেঙে ফেলতে পারে । উপন্যাসটির নাম ‘অলৌকিক প্রেম ও নৃশংস হত্যার রহস্যোপন্যাস’ বা ‘নোংরা পরির কংকাল প্রেমিক’, দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে ।
দুই
ফলত মলয় রায়চৌধুরীকে বাঙালি পাঠক এখন অনেক ভাবে চেনে। ষাট দশকের হাংরি আন্দোলনের পুরোধা পুরুষ, নতুন কবিতাধারার প্রবর্তক, গল্পকার, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, প্রাবন্ধিক, সমালোচক ও অনুবাদক; মায়, দু-একটি কাঁপা হাতের ড্রইং এবং স্কেচও আমরা দেখেছি। এই ভার্সাটাইল কাজকর্ম নিয়ে, তিনি একজন অধুনান্তিক ভাবুক। জীবনের যা কিছু ---- বাঁচা, বেঁচে থাকা, ভাষা সংস্কৃতি, শিক্ষা, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাজনীতি, ভূগোল, ইতিহাস, সাহিত্য ইত্যাদি প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রে তাঁর ভাবনাগত আনাগোনা। অথচ তিনি নিজেকে কোন বিশেষ অভিধায় চিহ্নিত করতে নারাজ। কেননা তিনি মনে করেন নিজেকে বা অপরকে অভিধায়িত করার যেসব শব্দাবলি চারপাশে সাজানো আছে, এখনো, সবই ব্রিটিশ মাস্টারদের ফেলে-যাওয়া বইপত্র, অভিধান আর আধুনিকতাবাদীদের বুকনি থেকে নেওয়া। উল্লেখ্য, নাগপুরের সুকুমার চৌধুরী ‘খনন’ থেকে প্রকাশ করেছিলেন মলয়ের জ্ঞানপুস্তিকা ‘পোস্টমডার্ন কালখণ্ড ও বাঙালির পতন’ ।
মলয় বিশ্বাস করেন শেষ বিশ্বযুদ্ধোত্তর দুনিয়ার ও দেশভাগোত্তর বাঙালির যে হালচাল, রাজনীতি, প্রশাসন, অর্থনীতি তাতে সেরকম মডারনিস্ট স্পেশালাইজড ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠার সার-বীজ সব পচে-হেজে নষ্ট হয়ে গেছে। 'আধুনিকতা' ব্যাপারটাই এখন 'একখানি ধ্রুপদী জোচ্চোর', কবিতায় বলেছেন মলয়। বলেছেন তিনি, এতদিন, 'আধুনিকতা ভালো, নৈতিক, নান্দনিক, প্রগতিশীল, উন্নত, কাম্য, কল্যাণময় এমনতর ভাঁওতায় ভুলিয়ে রাখা হচ্ছিল বাংলা ভাষাকে।' এহেন সময়ে একজন সমাজ ও সময় সচেতন লেখক যা করতে পারেন, তা হলো, বিগ্রহ ভাঙার কাজ। মলয় রায়চোধুরীর বেশির ভাগ রচনায় হাতুড়ির সেই চিহ্ন আমরা দেখেছি। কোন ধর্মভীরুতা বা প্রলোভন তাঁকে এই ভাঙার কাজ থেকে নিরস্ত করতে পারেনি, না বিদ্যায়তনিক মাস্তানদের ঘাতক-ছুরি। সাহিত্য অকাদেমির পুরস্কার ও বহু লিটল ম্যাগাজিনের পুরস্কার সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেছেন মলয় ।
বাংলা ভাষায় প্রতিষ্ঠিত আধুনিক ও এঁদো চিন্তাভাবনা ও তার ভেক্টর প্রতিষ্ঠানের মুখে জোর থাপ্পড় মেরে তার গিল্টি-করা দাঁত উখড়ে দিতে চেয়ে মলয়ের লেখার জগতে প্রবেশ। আজীবন অর্জিত নিজের ভোগান্তি, অভিজ্ঞতা, পড়াশোনা আর প্রজ্ঞাকে অস্ত্র করে তিনি যা-কিছু প্রাতিষ্ঠানিক চিন্তা-উদ্ভূত, মেরে লটলট ধ্বসিয়ে ফেলতে চেয়েছেন। একজন কালচেতন, সদাজাগ্রত লেখক প্রতিষ্ঠানের সামনে কী ভীষণ প্রব্লেম্যাটিক হয়ে উঠতে পারেন, তার জলজ্যান্ত মিশাল মলয় রায়চোধুরী। তিনি বলেছেন, “একা লড়েছি, কেউ ‘হোক কলরব করেনি, কেউ সঙ্গে ছিল না, আদালত থেকে বেরিয়ে সারারাত হেঁটেছি কলকাতার রাস্তায়”।
নিজেকে কালচারাল বাস্টার্ড বলেছেন মলয়। নিজেকে বলেছেন, বাঙলার মূল সংস্কৃতিতে আউটসাইডার। তাঁর বিভিন্ন রচনা,গল্প ও উপন্যাসে আমরা তাঁর সেই জারজ উপাদানের সুসম্বদ্ধ রূপটি গড়েও নিতে পারি। মজার ব্যাপার হচ্ছে কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের অভিজ্ঞতাহীন, হতাশাখোর, তথাকথিত শিক্ষিত হায়ারক্লাস বুদ্ধিজীবীরা মলয়ের পশ্চিমবঙ্গ-হামলার মনসুবাটা ধরতে পারেননি, আর মলয় বেশিরভাগ তথ্য সংগ্রহ করেছেন পশ্চিমবঙ্গের গ্রামগঞ্জে ট্যুর করে । আমি নিজে তথা-অর্থে 'বহিরাগত' হওয়ার দরুণ স্থূল ও সূক্ষ্ম দু-নিরীখেই অনুধাবন করেছি পশ্চিমবঙ্গের প্রাক-বর্তমান তথা বর্তমান সাংস্কৃতিক ও রাজনীতিক কাঠামোর মূল স্বরূপ বিশ্লেষণে মলয় কিন্তু আগাগোড়াই খুব পুঙ্খানুপুঙ্খ, যার তন্নতন্ন প্রতিফলন তাঁর লেখাজোখায় দুরনিরীক্ষ্য নয়।
বাঙালির ভিড় থেকে, হরির লুঠ থেকে, বাঁধাধরা বঙ্গ-কালচার থেকে স্বেচ্ছাবিচ্ছিন্ন এবং সর্বোপরি ভারতবর্ষীয় হিন্দু-বাঙালি সংস্কারের সর্বোচ্চ পীঠ বলে কথিত কলকাতা থেকে ২৬০ কিমি দূরে পড়ে আছি বলেই আমার কাছে ইঁদুরের প্রতিটি লাফ আর চাল জলবৎ ধরা পড়ে। তথাকথিত 'প্রবাস'-যাপনের সুবিধে এটাই যে, নিজের সঙ্গে অন্যের সাদৃশ্য ও পার্থক্য হবহু ধরে ফেলা যায়। দেখতে পাই দ্বৈরাজ্যের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা এই বিশ্বচরাচর, তার প্রতিটি নড়ন ও চড়ন।
জীবনের বেশির ভাগ সময়, মলয় রায়চোধুরী মূল বঙ্গ-সংস্কারের বাইরে বাস করে এই একই মাইক্রো-দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলা ও বাদ-বাংলার সংস্কৃতিকে পর্যবেক্ষণ করেছেন। এখন, বার্ধক্যে, তিনি কলকাতার ফ্ল্যাট বিক্রি করে, বইপত্র-আসবাব বিলি করে দিয়ে, সস্ত্রীক মুম্বাইতে বাস করেন। তিনি দেখেছেন যে-বঙ্গসংস্কৃতিকে নিয়ে বাঙালির এত আত্মম্ভরিতা, গুমর আর বারফট্টাই ----- সেই বিশুদ্ধ বঙ্গসংস্কৃতির হদিশ পৃথিবীতে আজ কোথাও নেই। ইতিহাসের বিভিন্ন ধাপে নানা জাতি ও সংস্কারের,বিশেষত মুসলিম ও ইংরেজ বেনিয়ার শাসনে, সর্বোপরি ভৌগোলিক কাটছাঁট, দেশভাগ ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক স্পৃহার খপ্পরে পড়ে বাঙালি নিজের সর্বস্ব আজ খুইয়ে ফেলেছে। এমনকী, বিশুদ্ধ পশ্চিমবঙ্গীয় সংস্কৃতিও আজ মিথ মাত্র। ভারতবর্ষীয় বাঙালির কোন সংস্কৃতিই আজ অবশিষ্ট নেই; সময়ের চাপে সব উচ্ছন্নে গেছে। জন্ম নিয়েছে এক জগাখিচুড়ি কালচার। ছত্রখান সংস্কৃতি। বাঙালির পোশাক পাল্টেছে বহুদিন হল, বহু খোঁপা আর সিঁথি এখন বিদেশিনী হয়ে গেছে, এমনসব হেয়ারডু যা বাঙালি কস্মিনকালে ভাবেনি। পুরুষেরা তামুক দোক্তা বিড়ি গড়গড়া ছেড়ে সিগারেট বিয়ার ব্রাউনসুগারে মজেছে। যে-ফুটবলে বাঙালির নিজস্ব দাপ ছিল তা এখন আকখা ওয়ার্ল্ড খেলছে, বাঙালি লোকাল ট্রেনে আর রকে বসে খেলছে তিন-পাত্তি, টোয়েন্টি নাইন। বাঙালি টুসু ভাদু রবীন্দ্রসঙ্গীত ভুলে পাঞ্জাবি পপে মাজা দোলাচ্ছে। পড়াশোনা চাকরি ব্যবসা থেকে ক্ৰমে উৎখাত হতে হতে বাঙালির নিজস্ব সংস্কৃতি বলে যা রয়ে গেছে, তা হলো, রকে বসে বুকনি ঝাড়া, পরস্পর পেছনে লাগা, লেংগি মারা, মিথ্যে বলা, হীনমন্যতা, চা চপ ঝালমুড়ি, লোকনিন্দা, ভাইয়ে-ভাইয়ে হিংসে, কথায় কথায় মাথাগরম আর খিস্তিবাজি। পাশাপাশি শনি-শেতলার পুজো, তৃণমূল-সিপিএম, ভর্তির সিন্ডিকেট, জমিদখল, ফ্ল্যাটদখল, মোহল্লা-দাদাগিরি, আর দুগ্গাপুজোয় চাঁদা আর মোদো হুল্লোড়বাজি।
‘নামগন্ধ’ উপন্যাস শুরু হচ্ছে একটা সন্ত্রাস দিয়ে, মলয়ের এটা অমোঘ টেকনিক, ----- পাঠকের সামনে সন্ত্রাস ঘটিয়ে, তাকে তার মধ্যে হিঁচড়ে ঢুকিয়ে সন্ত্রস্ত করে, সন্ত্রাসের বিভীষিকা মেলে ধরা। বঙ্গ-কালচারের বর্তমান হাল বোঝাতে মলয় হাওড়া জেলার ভোটবাগানের লোহার কাবাড়িখানা, নদিয়া জেলার কালীগঞ্জের কাঁসা-পেতলের ভাংরি, বিভিন্ন জেলার আলুর কোল্ড-স্টোরেজ মন্তাজ করে ফুটিয়ে বঙ্গভুবন একাকার করে ফেলেছেন। 'মুসলমান রাজার আমলে যেমন ছিল তালুকদার দফাদার পত্তনিদার তশিলদার মজুমদার হাওলাদার, এই আমাদের কালে হয়েচে পার্টিদার, 'আজগালকার জমিদার'। নমঃশূদ্রদের খুন ধর্ষণ বাড়িঘর জ্বালিয়ে যখন তাড়ানো হয়েছিল খুলনার মাইড়া গ্রাম থেকে, পঞ্চাশ সনে, যুবক ভবেশকাকা রাতারাতি পালিয়ে এসেছিলেন কচি ফুটফুটে সৎ বোনকে কোলে নিয়ে। পুরনো বাড়ির পাড়ায় ইউনাইটেড রিহ্যাবিলিটেশন কাউনসিলের 'আগুন-খেকো নেতা' ছিল ভবেশকাকা, যিনি বিধান রায় ট্রামের ভাড়া এক পয়সা বাড়িয়ে দেওয়ার প্রতিবাদে ট্রামে আগুন ধরিয়ে দেন। তিরিশ বছর আগে আরামবাগি প্যাঁচে কংগ্রেসি আলুর দাম হঠাৎ বাড়লে, খাদ্য আন্দোলনের দিনগুলোয়, তুলকালাম করেছিলেন। দেশভাগের খেলাপে নারাবাজি করেছিলেন, 'হাতে পেলে জহোরলাল জিনহাকে চিবিয়ে পোস্তবাটা করে'।সেই ভবেশ মণ্ডল আজ মোকররি আর চাকরান মিলিয়ে বাহান্ন বিঘে জমি আর একলাখ কুইন্টাল ক্ষমতাসম্পন্ন মোহতাজ হিমঘরের অংশীদার। যিশুর / লেখকের মন্তব্য : 'আজকাল গ্রামগুলোর সত্যের স্বামীত্ব ভবেশকাকাদের হাতে।' আর 'চাষির মুখের দিকে তাকালে সর্বস্বান্তের সংজ্ঞা টের পাওয়া যায়।'
মলয় নিজেকে গদ্যকার সাব্যস্ত করতে আদৌ গল্প-উপন্যাসে আসেন নি। তবু, গোড়া থেকেই যেটা সচেতনভাবে করেছেন, গল্প-বানানোর প্রথাগত টেকনিক ও সিদ্ধ নিয়মগুলোকে বানচাল করে বাংলার চলে-আসা মূল সাহিত্যধারাকে একেবারে অস্বীকার করার চেষ্টা। ভাষার ক্ষেত্রেও মিথ, দুয়ো শব্দকলাপ ও পড়িয়ে-নেওয়ার যাবতীয় সরঞ্জাম ইস্তেমাল। এবং বিষয় পুরোপুরি অধীত, সংপৃক্ত, যেন রিচার্ডস ওয়ার্ক পড়ছি। যেমন, 'ডুবজলে', 'জলাঞ্জলি' আর 'নামগন্ধ' ---- এই ট্রিলজিতে মলয় এক-গোছের চাকরির জিগির এনেছেন, সেটা হল, টাটকা আর পচা নোট আলাদা করা, একশোটা নোটের প্যাকেট তৈরি করা, এভাবে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর, যেন, 'অর্থনীতির স্নাতক হবার এই-ই পরিণাম। অমন বিতিকিচ্ছিরি কায়িক শ্রম করবার জন্যে ওই অফিসটা চেয়েছিল অর্থনীতি গণিত কমার্সে ভালো নম্বর প্রাপক স্নাতক।' অন্যদিকে, আজন্ম শহরবাসী মলয় কীভাবে পশ্চিমবাংলার গ্রামাঞ্চলে পরিব্যাপ্ত রাজনীতি, অর্থনীতি, দুর্নীতি আর কালচার জরিপ করেছেন তা 'নামগন্ধে' পড়ে থ মেরে যায় পাঠক। এই ভেবে যে কী করে পারেন! রীতিমত 'আলু-সমাজ-নাম'গুলোর গন্ধতালাশ। প্রান্ত গন্ধ।' কাহিনী বা নাটক সেখানে ন্যূন, আগেই বলেছি, বরং তা ঘনিয়ে ওঠার সম্ভবনা দেখা দিলে মলয় তা নিরাসক্ত ও নির্মোহ মনে ভেঙে দিয়েছেন। অন্বেষণের মেধা প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে পাতায়-পাতায়, বিশেষত উপন্যাসের শেষ দিকটা মার্ভেলাস। খোদ মলয়ের জীবন যেমন, উপন্যাসও তেমনি ----- জীবনেরই, অথচ প্রথানুগতের বাইরে। জীবনেরই ছোট ছোট খণ্ড, জীবনের সমাহার যেন, সম্পূরক। যেমন একযুগ পর ভবেশকাকার। বোন খুশিদিকে দেখে অপ্রত্যাশিত ধাক্কায় নির্বাক আনন্দে ছারখার হয়েছে যিশু। 'পঞ্চাশ বছরের একজন বালিকাকে কাছে পাবার ক্ষমতাকে দুর্জয় করে তুলতে, উঠে বসেছিল যিশু।' ভোগদৃশ্যটা অবিস্মরণীয় ----- 'প্রশ্রয়প্রাপ্ত যিশু গনগনে ঠোঁট বুলায়, রুদ্ধশ্বাস, ত্রস্ত। সিনেমা দেখে, টিভি দেখে, উপন্যাস পড়ে মানুষ-মানুষীর যৌনতার বোধ কলুষিত হয়ে গেছে, সর্বজনীন হয়ে গেছে। খুশিদির জৈব-প্রতিদান, বোঝা যাচ্ছে, সেই অভিজ্ঞতায় নিষিক্ত নয়। থুতনির টোল কাঁপিয়ে, ফুঁপিয়ে ওঠে খুশিদি; বলল, আয়, ভেতরের ঘরে চল যিশকা।'
আর, যেজন্য এই উপন্যাসের জিগির। মলয়ের লক্ষ্য গপ্পো বলা নয়, উপন্যাস গড়া নয় ---- ভাষা নির্মাণ। যেন, বাংলা গদ্যকে সশক্ত বনেদ পাইয়ে দিতেই তুখোড় কবিতাবাজ মলয় গদ্যের বাদাড়ে এসেছেন। গদ্য, যা বাঙালির যতিচিহ্ন। সমস্ত আবেগময়তাকে জোর ধাক্কা মেরে, থুয়ে রেখে, বাংলা গদ্যভাষাকে আরও শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করাতে মলয় মরিয়া। অন্তত নামগন্ধ বাবদ আমার তরফ থেকে স্বতোচ্ছ্বাস মারহাবা।
 অজিত রায় | 27.58.255.50 | ১০ আগস্ট ২০২১ ১৯:৪০734852
অজিত রায় | 27.58.255.50 | ১০ আগস্ট ২০২১ ১৯:৪০734852মলয় রায়চৌধুরী, তাঁর সাহিত্য, হাংরি আন্দোলন ও বন্ধুরা - অজিত রায়
সামান্য অভুয়িষ্ট ক্ষুধিত প্রজন্মের কবি ও কবিতা নিয়ে একটা আচাভুয়া লেখা লিখেছিলুম বছর পনেরো আগে, এক মফসসলি কাগজে । সেই শুরু । সেদিনের সেই সব্রীঢ় আত্মপ্রতর্ক থেকে প্ররোচিত হই হাংরি সিসৃক্ষার কলিন অধ্যয়নে । আর পরপর পরিচিত হতে থাকি মলয় রায়চৌধুরী, দেবী রায়, সুবিমল বসাক, উৎপলকুমার বসু, ফালগুনী রায়, সুবো আচার্য, করুণানিধান মুখোপাধ্যায় প্রমুখ হাংরি আন্দোলনের প্রতিভূ এবং তাঁদের সজ্ঞাননা-সম্ভূতির সঙ্গে ।
এঁদের মধ্যে, আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা আর বাংলা আভাঁগার্দ সাহিত্যের প্রধান স্রষ্টা মলয় রায়চৌধুরী সম্পর্কে আলাদা কথা আছে । আলাদা, কেননা, আমার মনে হয়েছে, মলয়ই প্রথম, যিনি বাংলা সাহিত্যের প্রতিষ্ঠিত এঁদো চিন্তাভাবনা আর তার ভেক্টর প্রতিষ্ঠানের মুখে জোর থাপ্পড় মেরে তার গিল্টি করা দাঁত উখড়ে তার ভেতরকার মালকড়ি ফাঁস করে দিতে চেয়ে লেখালিখির জগতে এসেছিলেন । মলয় এসেছিলেন এমন এক মিলিউ থেকে যেখানে বঙ্গসংস্কৃতির কোনো শিসই গজাবার নয় । জীবনের অনেকরকম শিক্ষা থেকে বঞ্চিত থাকতে হয় সেখানে । বিহারের ভয়ঙ্কর কুচেল অধ্যুষিত বাখরগঞ্জ বস্তিতে অতিবাহিত শৈশব । টায়ার ছোটোবেলা অতিক্রান্ত মুসলিম অধ্যুষিত দরিয়াপুর মোহল্লায় । সেই অস্বাচ্ছন্দ্য, অখল জ্বলা, ক্ষোভ আর বিদ্রোহকে বুকে নিয়ে তাঁর বেড়ে ওঠা । সংস্কৃতির একেবারে নিচেকার পাদানি থেকে আসা, নিম্নবিত্ত থেকে মধ্যবিত্তে ওঠার প্রতিটি মানুষী কসরতের সাক্ষী, স্পেংলারের সংস্কৃতি ও অবক্ষয়কালীন সর্বগ্রাস তত্বে তা-খাওয়া একজন বাইশ-তেইশ বছরের কৃষ্টি-দোগলা বা কালচারাল বাস্টার্ড লেখালিখির মঠে এলে যা ঘটবে, সেটা তো রফা হয়েই আছে ।
বাংলা সাহিত্যের, বিশেষত কবিতায় চলে আসা ন্যাকাচিত্ত পিলপিলে গীতিধর্মিতার প্রতি প্রচণ্ড বিরক্তি, ক্ষোভ আর প্রত্যাখ্যানসহ নতুন একটা কিছু করার ছটফটানি তিনি যখন সবে টের পাচ্ছেন, তখন তিনি পাটনা ইউনিভার্সিটিতে অর্থনীতির পড়ুয়া এবং মার্কসবাদ ও কবিতায় গভীরভাবে আক্রান্ত । তিরিশের পর চল্লিশ দশক থেকেতাঁর কাছে সমস্ত বাংলা কবিতাই যেন জোলো ঠেকছে । পঞ্চাশও নিজের ল্যাসল্যসানি সমেত কুণ্ডলী মেরে বসতে চাইছে । মলয় দেখলেন কবিতাকে আর এভাবে চলতে দেয়া ঠিক হবে না । বদল চাই । ফেরাফিরি চাই, তরমিম চাই । স্হিতাবস্হার বিরুদ্ধে আন্দোলন চাই । মলয়ের মাথায় গড়ে উঠল আন্দোলনের জিগির । আচমকা একদিন ইংরেজি পদ্যের বাবা জিওফ্রে চসারের এক টুকরো "ইন দি সাওয়ার হাংরি টাইম"এর মধ্যে খুঁজে পেলেন 'সমকালের অবধারিত সংজ্ঞা' । অসওয়াল্ড স্পেংলারের প্রাগুক্ত তত্বে আরোপ করলেন চসার কথিত সেই হাংরি ভাবনার দ্যোতনা । নিজের প্রজন্মের নাম দিলেন 'হাংরি' ।
প্রাথমিক পর্যায়ে মলয় পেয়েছিলেন দু'জনকে । হারাধন ধাড়া ওরফে দেবী রায় এবং শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে । পঞ্চাশের কবি হিসাবে শক্তি তখনই প্রতিষ্ঠিত । মলয়ের চিন্তাভাবনায় উৎসাহিত হয়ে শক্তি পাটনা থেকে ফিরে 'ছোটোগল্প' পত্রিকায় লিখলেন "ক্ষুৎকাতর আক্রমণ", আর বিনয় মজুমদারের 'ফিরে এসো চাকা'র সমালোচনা করতে গিয়ে সম্প্রতি কাগজে লিখলেন "হাংরি জেনারেশন সংক্রান্ত প্রস্তাব"। এ-দুটিই ছিল মলয়ের পরিকল্পনার প্রাথমিক ভাষ্য । পরে কেউ-কেউ, এবং শক্তি নিজে হাংরি আন্দোলনের স্রষ্টা হিসাবে শক্তি চট্টোপাধ্যায় নামটি চালাতে চেয়েছিলেন । সে ভিন্ন কথা । ১৯৬১ সালের নভেম্বর নাগাদ 'হাংরি জেনারেশন' নামে ১/৮ ডবলক্রাউন সাইজের কাগজের ইস্তাহারটি প্রকাশ পায়, তাতে বার্জাস টাইপে ছাপা হয়েছিল 'স্রষ্টা : মলয় রায়চৌধুরী, নেতা: শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদক : দেবী রায়' । আত্মার অশ্রুত ছটফটানিসহ যে মূলবার্তা মলয় এই ইস্তাহার মারফত প্রচার করতে চেয়েছিলেন, তা হল : "কবিতা এখন জীবনের বৈপরীত্যে আত্মস্হ । সে আর জীবনের সামঞ্জস্যকারক নয়, অতিপ্রজ অন্ধ বল্মীক নয়, নিরলস যুক্তিগ্রন্হন নয় । এখন, এই সময়ে, অনিবার্য গভীরতার সন্ত্রস্তদৃক ক্ষুধায় মানবিক প্রয়োজন শেষ । এখন প্রয়োজন অনর্থ বের করা, প্রয়োজন মেরুবিপর্যয়, প্রয়োজন নৈরাত্মসিদ্ধি । প্রাগুক্ত ক্ষুধা কেবল পৃথিবী বিরোধিতার নয়, তা মানসিক, দৈহিক এবং শারীরিক । এ-ক্ষুধার একমাত্র লালনকর্তা কবিতা । কারণ কবিতা ব্যতীত কি আছে আর জীবনে !...কবিতা বলে যাকে আমরা মনে করি, জীবনের থেকে মোহমুক্তির প্রতি ভয়ঙ্কর আকর্ষণের ফলাফল তা কেবল নয় । ফর্মের খাঁচায় বিশ্বপ্রকৃতির ফাঁদ পেতে রাখাকে আর কবিতা বলা হয় না । ...ইচ্ছে করে, সচেতনতায়, সম্পূর্ণরূপে আরণ্যকতার বর্বরতার মধ্যে মুক্ত কাব্যিক প্রজ্ঞার নিষ্ঠুরতার দাবির কাছে আত্মসমর্পণই কবিতা । ছন্দে গদ্য লেখার খেলাকে কবিতা নাম দিয়ে চালাবার খেলা এখন শেষ হওয়া প্রয়োজন । টেবলল্যাম্প ও সিগারেট জ্বালিয়ে, সেরিব্রাল কর্টেকসে কলম ডুবিয়ে, কবিতা বানাবার কাল শেষ হয়ে গেছে । এখন কবিতা রচিত হয় অরগ্যাজমের মতো স্বতঃস্ফূর্তিতে । সেহেতু ত্রশ্নু বলাৎকারের পরমুহূর্তে কিংবা বিষ খেয়ে অথবা জলে ডুবে 'সচেতনভাবে বিহ্বল' হলেই, এখন কবিতা সৃষ্টি সম্ভব ।...শখ করে, ভেবে ভেবে, ছন্দে গদ্য লেখা হয়তো সম্ভব, কিন্তু কবিতা রচনা তেমন করে কোনো দিনই সম্ভব নয় । অর্থব্যঞ্জনাঘন হোক অথবা ধ্বনি পারম্পর্যে শ্রুতিমধুর, বিক্ষুব্ধ প্রবল চঞ্চল অন্তরাত্মার ও বহিরাত্মার ক্ষুধা নিবৃত্তির শক্তি না থাকলে, কবিতা সতীর মতো চরিত্রহীনা, প্রিয়তমার মতো যোনিহীনা, ঈশ্বরীর মতো অনুন্মেষিণী হয়ে যেতে পারে।"
বাংলা কবিতাকে চরিত্রহীনা হয়ে যাওয়া থেকে বাঁচাবার এ ছিল এক অভিনব আয়োজন ।এই আনকা নওল মতধারা থেকেই হাংরি আন্দোলনের পথচলা শুরু। যা পরবর্তী দিনে খাড়া করে বাংলার শক্তমুঠো প্রতিভাবান শর্করীবাজদের এক দীর্ঘ রিসালা । মলয়ের একক ভাবনা ছড়িয়ে পড়ে গোষ্ঠীচেতনায় । ভবিষ্যত কর্মসূচি ঠিক করে নেবার জন্য দরকার হয় নির্নায়ন নিয়মাবলীর । সেই তাগিদে মলয় তৈরি করেন একটি চোদ্দদফা ইশতাহার, যা থেকে ফুটে ওঠে আন্দোলনের নিখাঁজ রূপরেখা এবং উদ্দেশ্য, কী আর কীভাবে লিখব-র উত্তর । পূর্ণাবস্হায় ইগোর ক্ষমাবর্জিত প্রকাশ, খাস লহমায় বিস্ফরিত আত্মার ইঙ্গিত পুরোপুরি শব্দবন্ধে ও প্রকাশভঙ্গীতে । ঐতিহ্য ও গতানুগতের প্রতিবাদ । এবং তার ভাস্বরতা প্রাত্যহিক জবানে । বাঁধাধরা মূল্যবোধের খেলাপে জেহাদ । ধর্ম অহিফেন, রাজনীতি বন্ধ্যা । মূলধন শুধু কবিতা । সেই কবিতাই হাংরিদের হাতিয়ার হল । সশস্ত্র হাংরিরা ছড়িয়ে পড়লেন চারিদিকে । রাস্তায় ঘাটে দোকানে বাজারে অফিসে দেওয়ালে পোস্টারে ...সর্বত্র হাংরি হাংরি হাংরি । প্রথম প্রতিষ্ঠানবিরোধিতা ।
হাংরি কোনও 'ইজম' ছিল না । ছিল একটা স্টাইল বা আইডিয়া । তবে স্ফীত অর্থে আন্দোলন কথাটা অনেকের পছন্দ । বলতে পারি একটা ঘটনা, বাংলা সাহিত্যে সেভাবে যা আগে কখনো ঘটেনি । বাংলা সাহিত্যের তথাকথিত মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন অনাদৃত এক উপদ্রুত এলাকা থেকে বিশাল একটা ঢেউ, উঠে, আছড়ে পড়েছিল ইজি গোইং সাহিত্যের প্যালপিলে ল্যাসলিসে মসৃণ চত্বরে । সমাজের একেবারে নিচুতলার ভাষা ও ভাবনাকে সাহিত্যের কাছাকাছি নিয়ে আসার, পক্ষান্তরে বাংলাসাহিত্যের লিরিকফুলের সাজানো বাগানকে তছনছ করে নতুন প্রতিমান প্রতিষ্ঠার তাগিদে হাংরি ছিল প্রথম আর তখনও অব্দি একমাত্র বৈপ্লবিক সমীহা । পাশল অর্থে একে "আন্দোলন" বলা হচ্ছে, সেহেতু তা শুরু হয়েছিল একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য, গোষ্ঠী আর প্রস্তুতি নিয়ে । যার লিখিত ম্যানিফেস্টো ছিল। এবং যার অনেক ইশ্যু, সেই ডামাডোল প্রধান ষাট দশকে বাঙালি কবি-গদ্যকারদের এমনকি পঞ্চাশ দশকের কবিদের একাংশকেও তুমুলভাবে নাড়া দিয়েছিল -- যার দরুণ সুদীর্ঘ কাতার । প্রবল ঘুর্ণাবর্ত্ম ।
এটা ঠিক যে ঐ সময়ে মলয় ও তাঁর সহযাত্রীদের কজন মিলে এমন কয়েকটি কাণ্ড করেছিলেন, যার সঙ্গে আন্দোলনের ঘোষিত উদ্দেশ্যের কোনও রকম সরোকার ছিল না, এবং যার দরুণ গঙ্গাজলি সাহিত্যের কোল-আলো-করা কবি-লেখকরা আন্দোলনের ওপরই দারুণ খচে যান । কিন্তু বলা বেশি, বাড়িতে মর্মান্তিক দুর্ঘটনার ভুয়ো খবর দিয়ে জনৈক বাজারি লেখকের অফিসে ফোন, বিভিন্ন পশুপাখি ভাঁড় আর শ্বাপদ-শয়তানের মুখোশ কিনে প্রাতিষ্ঠানিক নোকরদের নামে পাঠানো, পাবলিক ল্যাভাটরিগুলোর দেওয়ালে উদ্ভট পোস্টার সাঁটা বা বাঙালি কবিদের বংশপঞ্জি প্রচার -- এসবে নয়, প্রতিষ্ঠানের লোকেরা ভয় পেয়েছিলেন হাংরিদের যা ছিল আসল হাতিয়ার : অনুশাসন থেকে মুক্ত ছোটোলোকি শব্দের ব্যবহার আর নিচুতলার মনোভাবের ছোঁচালো সীবনীটিকে। আর সেটাই ছিল আন্দোলনের পজিটিভ দিক ।
আসলে হাংরিরা যে ভাষায় ও চেতনায় গদ্য-পদ্য নিয়ে এসেছিলেন, তা ছিল আমাদের এতোদিনকার বুর্জোয়া সংস্কারের বাইরে । আন্দোলনের মেজর কবি-লেখকরা প্রায় প্রত্যেকেই এসেছিলেন বাঙালি নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে, সেই স্তরের যাবতীয় শিক্ষা-সংস্কার নিয়ে । শক্তি, সন্দীপন, উৎপল, সমীর, সুবো, মলয়, ত্রিদিব, দেবী, ফালগুনী, অবনী, অরনি, রবিউল, বাসব,বাসুদেব, সুবিমল, সুভাষ, প্রদীপ, শৈলেশ্বর প্রমুখের সবার সম্পর্কেই এ তথ্য লাগসই । সুতরাং তাঁদের আত্মার ঘোর আততি, স্বদন্দ্বের সিনথেসিস থেকে গদ্য ও কবিতাকে রূঢ় কর্কশ ছালে সজ্জিত করা । জীবনকে প্রায় চিনিয়ে দেয়া, স্বাধীনতার তলানিটুকু পর্যন্ত উজাড় করে স্মাৎ করা, দৈনন্দিন হাড় পুঁজ রক্ত কফ উচাটন ফন্দিহীন ভাবে গদ্য ও কবিতায় আনা দগদগে আত্মবোধ ও অহং, মগজকে সম্বল করে সৃজন -- এসবের কোনো কিছুর মধ্যেই কোনও সিউডোপনা, পাঁয়তাড়া, বারফট্টাই বা কারাসাজি ছিল না । বাংলা সাহিত্যে এই জিনিস আলবৎ নতুন । আমাদের বুর্জোয়া সংস্কারের সম্পূর্ণ বিপরীত । আসলে বাংলা গদ্য ও কবিতাকে তার কৃত্রিমতার খোলস ছাড়িয়ে একটা পরাদর্শী আর শক্ত সবল বনেদ পাইয়ে দেবার জন্যে হাংরিদের এ ছিল এক ভয়ঙ্কর আয়োজন ।
ভয়ঙ্কর হলেও সাহিত্যের তাতে ক্ষতি হয়নি । কেননা অতি ভদ্র আর ঝুঁকিহীন মন্তব্যে যাঁরা বিশ্বাসী তাঁরাও প্রকারান্তরে স্বীকার করেছেন যে, বাংলা কবিতা নিয়ে উত্তর-রবীন্দ্রকালে নিরীক্ষার ব্যাপারটা হাংরিরা প্রথম চালু করেন । আর পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সাহিত্যের ক্ষতি হয় না । বরং তন্বিষ্ঠ গবেষণা একদিন বলবে, এতে করে কয়েক ধাপ হঠাৎ দুম করে এগিয়ে গিয়েছিল বাংলা কবিতা । পরবর্তীকালের বাংলা কবিতায় এর সুফল দুর্লক্ষ্য নয় । বিশেষত সত্তর-আশির সময় থেকে কবিতাক্ষেত্রে একটা মৃদু প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে । কবিদের একটা গণ্য অংশ অন্তত লিরিকাল ধাঁচ ছেড়ে বেরিয়ে আসছেন, হাংরির তত্বভাবনা অনেকের লেখায় পরোক্ষভাবে কাজ করেছে এটা কম কথা নয় । বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ত্বকে পচন ও পয়মালের ঘা দগদগ করছে যখন, সেই মুহূর্তে একদল তেজি, রাগি আর প্রতিভাবান যুবক নিজেদেরকে উচ্ছন্নে দিয়ে বাংলা সাহিত্যের ভেজানো কপাটে দিতে পেরেছিলেন একটা জোর দস্তক, এটা ঊন বা অবম তথ্য নয়। যে কারণে জন্মকালেই হাংরি আন্দোলনকে ধ্বংস করার চক্রান্ত, দুষ্প্রচার, অতর্কিত হামলা, পুলিশি হুজ্জত, কোর্ট কেস, মুচলেকা লেখানো, চাকরি থেকে বরখাস্ত, ট্রান্সফার ইত্যাদি স-অব ঘটেছে একাদিক্রমে এবং পরপর ।
এসবের দরুণ এবং আরও কিছু পরোক্ষ ও পপত্যক্ষ কারণে এই আন্দোলনের নখদন্ত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের শরীরে পিরেনিয়্যেল আঁচড় কেটে অচিরেই ধাবাড় মেরে যায় । ১৯৬১ থেকে ১৯৬৫কেই বলা যায় হাংরি আন্দোলনের সবচেয়ে উত্তেজনাকর আর ঘটনাবহুল অস্তিত্বকাল । কিন্তু অন্যদিকে জেব্রা, উপদ্রুত, ক্ষুধার্ত, ফুঃ, উন্মার্গ, চিহ্ণ, প্রতিদ্বন্দ্বী, ওয়েস্ট পেপার, স্বকাল, ব্লুজ, জিরাফ প্রভৃতি কাগজকে ঘিরে পাশাপাশি শম্ভু রক্ষিত, আলো মিত্র, দেবী রায়, মলয় রায়চৌধুরী, ফালগুনী রায়, প্রদীপ চৌধুরী, বাসুদেব দাশগুপ্ত, সুবিমল বসাক, সুভাষ ঘোষ, সুবো আচার্য, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ত্রিদিব মিত্র, তপন দাশ, অলোক গোস্বামী, রাজা সরকার, অশোক চট্টোপাধ্যায়, শঙ্কর দে, বিকাশ সরকার, মলয় মজুমদার, জীবতোষ দাশ, অনিল করঞ্জাই, করুণানিধান মুখোপাধ্যায়, অরুণেশ ঘোষ প্রমুখেরা গড়ে তুলেছিলেন হাংরি সিসৃক্ষার আরেকটি চক্র । এবং আন্দোলনের উত্তেজনা থম মেরে গেলেও, তারপরেও সেই সব সেরকশ আর গেঁতো মৌমাছি , ক্ষুধার্ত, প্রতিদ্বন্দ্বী, সকাল, ফুঃ, চিহ্ণ, জিরাফ, আর্তনাদ, কনসেনট্রেশন ক্যাম্প, ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি রেফ্লুয়েন্ট চাককে আঁকড়ে কিছুকাল শর্করাবাজি চালিয়ে গেছেন বটে, কিন্তু আসর আর জমেনি ।
আসলে সাহিত্যের আন্দোলন মাত্রেই হ্রস্বজীবি । হাংরি আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়া সমস্ত কবি-লেখকদের কথা যদি ধরি, সকলে কোনো নির্দিষ্ট সমাজ-স্তর থেকে আসেননি । তাঁদের মধ্যে নান্দনিক দৃষ্টিবৈভিন্ন্য ছিল, যা আন্দোলনের শেষাশেশি ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠেছিল । এ-বাদে ব্যক্তিজীবনের উচ্ছৃঙ্খল বিষাদ, উপরতস্পৃহা, আর নিরাশাও চাগাড় দিয়ে উঠেছিল । এ-কথা অনস্বীকার্য যে তত্ববিশ্বের দিক থেকে প্রাথমিক পর্যায়ে সবাই এক জায়গায় জড়ো হয়েছিলেন, কিন্তু তবু কবিতার জন্ম ফ্রম এ স্ট্রং পার্সোনাল নিড, র্যাদার দ্যান ফ্রম এনি থরো আনডারস্ট্যানডিং অফ অ্যান আইডিওলজি --- ফ্রয়েডিয় মতবাদের গুরুত্ব ও প্রভাব কম হয়ে যায় না ।
ছেষট্টির গোড়া থেকেই শরিকরা বয়স-অভিজ্ঞতা-চিন্তা মোতাবেক নিজের-নিজের বৌদ্ধিক ও রাজনৈতিক রাস্তা বেছে নিতে শুরু করেছিলেন । প্রকৃত সাংস্কৃতিক নিউক্লিয়াসের অভাবে আন্দোলনকে বাঁচিয়ে রাখা মুশকিল হয়ে পড়ে । তারপর আন্দোলন সম্পর্কে ভাবি-প্রজন্মের মনে দুরোধিগম্যতা, খটমটি, ভ্রান্তব্যাখ্যার যথেষ্ট সুযোগ জিইয়ে রেখে আন্দোলনের প্রভাব ডবলমার্চ করে ফিরে গেল ভাটায় । আন্দোলন পুরোপুরি বানচাল হয়ে গেলে কেউ কেউ তিন সত্যি কেটে সাইড নিয়ে নিলেন, প্রচল ধারায় লেখনীপাত শুরু করলেন, কেউ-কেউ মার্কসবাদী রাজনীতির ঝাণ্ডাতলে গিয়ে সাময়িক স্বস্তি লাভ করলেন, কেউ-বা আশ্রয় নিলেন ধর্মের, আবার কেউ-বা লেখালিখি ছেড়ে, বন্ধুবান্ধব ছেড়ে, সমস্ত যোগাযোগ ছিন্ন করে চলে গেলেন অজ্ঞাতবাসে । চিরতরে হারিয়ে গেলেন কেউ-কেউ । কিংবা যোগ দিলেন অ্যাকাডেমি ও মিডিয়ার তাঁবুতলে ।
পঁয়ত্রিশ বছর কেটে গেল তারপর । পঁয়ত্রিশ বছর । নিছক কম সময় নয় । এ নিছক ঘড়ির কাঁটার টিক-টিক সরে যাওয়ার বা ক্যালেণ্ডারের তারিখ বদল নয় । অনেক বদল ঘটে গেছে এই সময়ে । এর আগে অব্দি কোথাও না কোথাও, কোনোখানে, একটা স্হৈর্য, স্হিতিবোধ, বিশ্বাসের বলয়ে জীবনকে সংবৃত করে রেখেছিল, চতিস্পার্শস্হ মসৃণ জীবনযাত্রায় জীবনমোহরের একটা স্হির অলিকল্পিত উপলব্ধি সৃজনশীল মানুষের মনে সদা জায়মান থেকেছে । কিন্তু এখন, তরবারীর সুমসৃণ যখন ফালি-ফালি করে কেটে ফেলছে আমাদের জোড়াতালি অস্তিত্ব, হঠাৎ-হঠাৎ টের পাচ্ছি সমুখে সমূহ অস্হিরতা, এখন এই অস্হির দজ্জাল সময়ে সুস্হতার মাঝে বিধ্বংসী ভালোবাসা আর বিপন্ন মগজজাত ক্ষিপ্ত চেতনা নিয়ে 'লড়াই' জেতার উপকিঞ্চিৎ লজিকটুকুও বেমালুম হাপিস । এ-সময়ে হিটলার হয়ে দুনিয়াটাকে দাপানো সহজ যদি-বা, কিন্তু নিছক কলমী বিদ্রোহ করে কিছু গড়তে পারার সম্ভাবনা বুঝি আর নেই । যাকে নিয়ে আমার চিন্তা, যার মুখ একটু-একটু করে সোজা রাখতে চাওয়া -- তার জন্য, আমাদের অভিজ্ঞতা বাৎলে দিচ্ছে, বাস্তিল থেকে শুরু করে গ্লাসনস্ত-পেরেস্ত্রৈকা কোনো কিছুতেই প্রাসাদশীর্ষ থেকে বদল সম্ভব নয় । এবং যা বিপ্লব, মত-সাপেক্ষে তা পপতিবিপ্লব । যুদ্ধ কবেই হেজে গেছে, এখন খড়গের শানানো ধারে খয়েরি পোঁচড়, গিলোটিনে আলপনা বিলাসিতা । 'প্রতিবাদ' শব্দটাকে অভিধান থেকে লোপাট করে দেবার দিন আজ । আশার পাছায় ঘাঘরা বেঁধে কোঠায় ছেড়ে দেবার দিন ।
তো ? এরকম সময়ে, এই প্রেক্ষিতে তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগে বাংলা সাহিত্যের প্রচলিত সংস্কারের বিরুদ্ধে, তার পচা ভিত্তিকে উৎখাত করার একান্ত অভীপ্সায় দুর্বিনীত আসর যিনি করেছিলেন, বিশ-তিরিশ বছর বাদে লেখালিখির জগতে প্রত্যাবর্তন করতে চাইলেও, তাঁর কাছে প্রধান সমস্যাটা কী খাড়া হতে পারে ?এমনিতে পঞ্চাশের কবি-লেখকরা যাঁরা হাংরি আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন, আন্দোলন ফুরিয়ে যাবার পর নিজেদের চরিত্র মোতাবেক লিখে আসছিলেন । শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের এতোলবেতোল জীবন শুরু হয়ে যায় আর তিনি ছদ্মনামে 'রূপচাঁদ পক্ষী' হয়ে যান, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় একটা নির্দিষ্ট গদ্য রেওয়াজ করতে করতে নিজস্ব শৈলীতে থিতু হন । বিদেশ থেকে ফিরে উৎপলকুমার বসুও কাব্যচর্চার নবাঞ্চল অব্যাহত রাখেন । ষাটের কবি-লেখক হিসেবে পরিচিত অশোক চট্টোপাধ্যায়, দেবী রায়, শৈলেশ্বর ঘোষ, অরনি বসু, অবনী ধর, বাসুদেব দাশগুপ্ত, সুভাষ ঘোষ, ফালগুনী রায়, শম্ভু রক্ষিত, প্রদীপ চৌধুরী, সুবো আচার্য প্রমুখের লেখালিখি থেমে থাকেনি এবং দেখা গেছে বয়স, অভিজ্ঞতা ও সিরিয়াসনেসের দরুন এঁদের কেউ-কেউ খুঁজে পেয়েছেন নিজস্ব ফর্ম, চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গীতে একজন আলাদা হয়ে উঠেছেন অন্যজনের থেকে । অর্জন করেছেন চারিত্র্য, আর বাংলা সাহিত্যে এনেছেন ভিন্নতর আধার-আধেয় !
মলয় রায়চৌধুরীর কেসটা এঁদের চেয়ে আলাদা । এবং আপাত-জটিল । বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির পীঠস্হান হিসেবে বিজ্ঞাপিত কলকাতার ধুলো মলয়ের পায়ের তলায় সেভাবে লাগেনি, যেখানে, অনেকে মানতে না চাইলেও, অনেক ধুলো । কলকাতার একটা পুশিদা ক্লোমযন্ত্র আছে যা বামুন আর চাঁড়ালকে শুঁকে চিনতে পারে । কলকাতা মলয় রায়চৌধুরীকে নিজের দাঁত দেখিয়ে দিয়েছিল । কলকাতা তাকে বুঝিয়ে দিয়েছিল, তুমি আমাদের লোক নও । তুমি একটা কৃষ্টিদোগলা । তোমার কলমে ছোটোলোক রক্ত । তোমার টেক্সট আলাদা । আলাদা থিসরাস । তফাত হটো তুমি । এবং, কলকাতা মলয়ের সঙ্গে সমস্ত শরোকার ছিন্ন করে । ভয়ে কোনও সম্পাদক তার কাছে আর লেখা চান না । বন্ধুবান্ধবদের চিঠি আসা বন্ধ হয়ে আসে ক্রমশ, এবং যারা মুচলেকা দিয়েছিল তারা সবাই স্লিপ করে যায় । লেখা ছাপানো অসম্ভব হয়ে পড়ে । এই বীভৎস যন্ত্রণা, একাকীত্ববোধ, অপমান একমাত্র কলকাতাই দিতে পারে । এই যন্ত্রণা, অপমানই মলয় রায়চৌধুরীকে লেখালিখি থেকে নির্বাসন-ভোগের আরেক অব্যক্ত যন্ত্রণার দিকে ঠেলে দিয়েছিল মলয়কে । ২৭ জুলাই ১৯৬৭, মানে, হাইকোর্টের রায়ে বেকসুর খালাস পাওয়ার পরদিন থেকে মলয় কবিতা লেখা ছেড়ে দেন । সবায়ের সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন করেন । আর নিজেকে ক্রমশ অসীম একাকীত্বে ঘিরে ফ্যালেন । প্রশাসন ও প্রতিষ্ঠানের দুর্গদ্বার থেকে অপরিগৃহীত হয়ে লেখার জগৎ থেকে একান্তে অপসৃত হয়ে স্বরচিত নির্জনতার এক সুচারু এরিনায় নিজেকে বন্দী রেখে, রাইটার্স ব্লকের অখল জ্বালা ভোগ করা -- হাংরিদের মধ্যে এটা একমাত্র মলয়ের ক্ষেত্রেই ঘটেছে ।
আত্মবিবাসনের সেই বিবিক্ত দিনে, ১৯৬৮-এর ডিসেম্বরে রাজ্য-স্তরের হকি খেলোয়াড় শলিলা মুখার্জির সঙ্গে উদ্বাহর সাময়িক স্বস্তি ফিরিয়ে আনে তাঁর জীবনে । জীবনের মতো ভেলকি জানে কে আর ! সে বারে-বারে মানুষকে ষাঁড়ের গোবর করে । চটকায় । ঘুঁটে বানিয়ে শুকোতে দেয় । আবার, পেড়েও আনে । জীবন লিখেওছে এমন ফিচেল কেলিকিন, যে কবিতা বোঝে না । মন বোঝে না । আদর্শ বোঝে না । আলোপিছল প্রতিষ্ঠানের মসৃণ করিডোর দিয়ে হাঁটিয়ে সটান তুলে দেয় আরাম, স্বাচ্ছন্দ্য আর কর্তৃত্বের সুনিপুণ এলিভেটরে । অর্থাৎ 'একদা আপোষহীন' এবং পরে 'অঙশভাক' এই ঐতিহাসিক গল্পের পুনরাবৃত্তি মলয়ের জীবনে ঘটাল সেই নর্মদ । এই ট্র্যাজেডির জন্যে আমরা ইতিহাস আর সময়কে বাদ দিয়ে বরাবর ব্যক্তিকে দায়ি করি, তাকে ব্যক্তির ট্র্যাজেডি হিসেবে চিহ্ণিত করে সৌমনস্য উপভোগ করি, সে আমাদের প্রবলেম ।
কিন্তু ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি এক অনৈতিহাসিক তত্ব । এ-খবর সত্যি যে বিবাহোত্তর প্রবাসে বিভিন্ন শহরে কিছুদিনের জন্য এলিট সংসারি হয়ে উঠেছিলেন মলয় রায়চৌধুরী । সৃজন, সাহিত্য, বইপড়া, বাংলা ভাষা ইত্যাদি থেকে আরও দূরে সরে থাকবার মতো সরঞ্জাম তখন মজুত । মৎসরী বন্ধুরা হয়তো এই জেনে কিঞ্চিৎ আরামও উপভোগ করছিলেন যে গার্হস্হ দায়িত্ব নির্বাহ করা ছাড়া মলয় "আর কিছুই করছেন না"। কিন্তু তাঁদের গুড়ে বালি নিক্ষেপ করে আশির দশকের গোড়ার দিকে আবার লেখালিখির জগতে তুমুল বেগে ফিরে এলেন মলয় রায়চৌধুরী ।
প্রত্যাবর্তিত মলয় রায়চৌধুরীর মধ্যে অনেক মাল, অনেক মউজ । মানে, দারুণ একটা রায়বেঁশে, হই হল্লা, তারপর নর্তকের আর কোমর-টোমর রইলো না, মলয়ের কেসটা সেরকম নয় । তিনি যে হাত-পা ছুঁড়েছিলেন, বেশ কিছু জ্যামিতিক পারফরমেন্স দেখিয়েছিলেন । বিশ বছর বাদেও দেখছি, সেই কোরিওগ্রাফিটা থেকে গেছে । দেখে-শুনে মনে হচ্ছে, গুঁতো দেবার তালেই ছিলেন যেন । আর গুঁতোবার আগে যেমন মাথা নিচু করে কয়েক পা পিছিয়ে যায় অগ্নিবাহন, তেমনি করে হয়তো-বা আবার করে অঙ্গহার দেখাবেন বলে খানিক জিরিয়ে নিচ্ছিলেন মলয় । কিংবা লেখা ছাপানো বন্ধ রেখে পরখ করে নিচ্ছিলেন তিনি টিকে আছেন, না উবে গেছেন ।
মলয় রায়চৌধুরী যে আবার নতুন করে লেখালিখি শুরু করেন, উনিশশো আশি-বিরাশি নাগাদ, তার পেছনে প্রাথমিক প্ররোচনা ছিল সত্তর দশকের বিশিষ্ট কবি, গদ্যকার ও 'কৌরব' পত্রিকার সম্পাদক কমল চক্রবর্তীর । কমল নাগাদে তাগাদা দিয়ে মলয়ের কাছ থেকে আদায় করেছিলেন এক গোছা মন্ময় পদ্য । আজকের এই ফিরে আসা হই-চইহীন নিরুত্তেজ উদ্দাস্ত-যমিত শান্ত অবাস্হ নিরুদ্বেগ ঠাণ্ডামাথা মলয় রায়চৌধুরীর মধ্যে সেদিনের সেই উত্তপ্ত অস্হির আন্দোলিত প্রবহস্রোতের মাঝে অবগাহনরত মলয় রায়চৌধুরীকে খুঁজতে যাওয়া গোঁয়ার্তুমি মাত্র । তবে, বুকের মধ্যে ঢেউয়ের সেই দাপানিটা আর নেই বটে, কিন্তু পানখ সাপের ফণাটা এখনও উদ্যত ( উল্লেখ্য, মলয় রায়চৌধুরীর ডাকনাম 'ফণা' ) । সেই কর্কশ আর গতলজ্জ ভাষা, নিলাজ শব্দাক্রমণের ফলাটা এখনও তেমনি পিশুন । আর তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নতুন করে বেড়ে-ওঠার অদম্য উৎসাহ, জেদ আর সামর্থ । যেন পুরোনো দখলতি হাসিল করতেই তাঁর ফিরে আসা ।
তবে গড়ে-ওঠা পর্বে, খুব বেশি কবিতা তিনি লেখেননি । ১৯৬১ থেকে ১৯৬৩ কালখণ্ডে লেখা কবিতার প্রথম সংকলনটি বেরিয়েছিল ১৯৬৩ সালে 'কৃত্তিবাস প্রকাশনী' থেকে, 'শয়তানের মুখ' নামে ( প্রচ্ছদ মেকসিকোর জনৈক চিত্রকর )। হাংরি আন্দোলনের বাইপ্রডাক্ট 'জেব্রা' পত্রিকা থেকে ১৯৬৫-এ বেরিয়েছিল দুটি দীর্ঘ কবিতা - "অমীমাংসিত শুভা" আর "জখম" । "জেব্রা" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল মলয়ের অ্যাবসার্ড নাটক 'ইল্লত', যাকে পরবর্তীকালে বলা হয়েছে 'পোস্টমডার্ন' -- নাটকটি 'বহুরূপী' পত্রিকার কুমার রায় এবং 'গন্ধর্ব' পত্রিকার নৃপেন সাহা প্রকাশ করতে অস্বীকার করেছিলেন, দুর্বোধ্য হিসাবে । পরে কবিতীর্থ প্রকাশনী হাংরি আন্দোলনের সময়ে লেখা তাঁর তিনটি 'হাংরি' নাটক 'নাটকসমগ্র' নামে প্রকাশ করেছে।
মলয় রায়চৌধুরীর প্রথম দিককার সমস্ত লেখা আমার পড়া হয়নি, বিশেষ করে ১৯৬২ সালে শক্তি চট্টোপাধ্যায় প্রকাশিত মলয়ের 'মার্কসবাদের উত্তরাধিকার' এবং 'বিংশ শতাব্দী' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত 'ইতিহাসের দর্শন'। যেটুকু পড়েছি, তাতে সব থেকে বেশি আক্রান্ত হয়েছি 'প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার'-এ। হাংরি জেনারেশন বুলেটিনের আগস্ট ১৯৬৪ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশ পেয়েছিল কবিতাটি, যা মলয়ের জীবনে, এবং তাঁর হাংরি বন্ধুদের জীবনেও, বয়ে এনেছিল প্রচণ্ড তুফান । আদালতে অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত 'প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার'-এ আমি খুঁজে পাই এক তরতাজা যুবকের আর্তি, অসহায়তা, যন্ত্রণা, আমর্ষ আর ক্লেদ । বাংলা কবিতার জমিতে গড়া প্রচলিত সংস্কারের গাঁথুনির ভিত নড়বড়ে করে দিয়ে জীবনচর্চার গূঢ় সত্য প্রকাশ করে বলেই কবিতাটি একই সঙ্গে মলয় রায়চৌধুরীর প্রথম পর্যায়ের কবিতা চর্চা আর হাংরি আন্দোলনের প্রতিনিধিত্বকারী শ্রেষ্ঠ মুখবন্ধ বলে বিবেচিত হওয়া উচিত । এ ছিল মলয়ের চেতন-অবচেতনের এক উজ্জ্বল প্রতিফলন ।
স্বীকার করা ভালো, মলয়ের সেইসময়কার বেশিরভাগ কবিতা পড়লে মনে হয় তাঁর স্বঘোষিত 'অরগ্যাজমের মতো স্বতঃস্ফূর্তিতে' যে লেখা বের হয়, তেমন-কিছু তিনি নামাতে পেরেছেন খুব কম । তাঁর বেশির ভাগ কবিতাকে মনে হয়েছে বানানো । শব্দ শরব্যতার দিকে তাঁর প্রচণ্ড ঝোঁক । একেকটা শব্দকে কোথায় কীভাবে কতোটা ফাঁক দিয়ে বসালে চমক খাবে পাঠক, যেন এই প্রবণতা থেকেই এক-একটি কবিতা তাঁর । এটা ঘটেছে, কেননা আদপে তিনি কবিতা গড়েন, বানান, তৈরি করেন । এবং যথেষ্ট সচেতন থেকে তাঁর নিজের কথায় 'একটা আইডিয়া কিছুদিন ধরে আমার মাথায় ঘোঁট পাকায় । কিছুটা ঘোরের মতো সেটা কাগজে নামাই । তারপর ঘষেমেজে কবিতাটা লিখি'। আসলে মলয় আগাগোড়া সুররিয়ালিজমকে বাহন করেছেন, অবচেতন ও স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টির কথা ভেবেছেন ঠিকই, কিন্তু সচেতনভাবে । তাঁর কথা হলো -- "সচেতনভাবে বিহ্বল হয়েই কবিতা লেখা সম্ভব"। অর্থাৎ মেধা-মননের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে আসবে কবিতা । যে-জন্যে তাঁর পরবর্তী কাব্যগ্রন্হের নাম 'মেধার বাতানুকূল ঘুঙুর', 'চিৎকার সমগ্র', 'যা লাগবে বলবেন'।
মলয় রায়চৌধুরী তাঁর নানা গদ্যে, সাক্ষাৎকারে, একটা কথা বেশ গুরুত্ব আর জোর দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন যে, হাংরি আন্দোলন বা হাংরি লেখালিখি আগাগোড়া সাবভারসিভ ছিল ( তাঁর বিরুদ্ধে আদালতে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ ছিল ), সুররিয়ালিজম বাদে তাতে অন্য কোনো বহিঃপ্রভাব ছিল না । কিন্তু গোড়ার দিককার তাঁর নিজের কিছু-কিছু কবিতায় বাহ্যিক প্রভাব সম্পর্কে অনেকে সন্দিহান । কবি পবিত্র মুখোপাধ্যায়, বাসুদেব দাশগুপ্ত প্রমুখ তাঁর 'অমীমাংসিত শুভা' ও 'জখম' পর্যায়ের নির্মাণগুলিতে দেখেছেন বিট কবিদের উচ্চকিত প্রভাব । মলয় এই আরোপের বিরুদ্ধতা করেছেন । আমি সেই বিতর্কের মধ্যে যেতে চাইছি না । শুধু বলব, প্রভাব জিনিসটা কি সত্যিই নক্কারজনক ? শুনেছি, অল আর্ট ইজ মাইমোসিস । আর কবির সৃষ্টি-প্রভায় 'প্রভাব' শব্দটি সবিশেষ অর্থবহ । সামান্য 'ইনফ্লুয়েন্স' শব্দে তা নিরূপেয় নয় । প্রভাব অর্থে 'প্রকৃষ্ট ভাব', তা পূর্বতনের হলেও ভিন্নতর কবিকল্পনায় নতুন করে 'হয়ে ওঠে' । আর হাংরি কবি-লেখকরা তো ছেনি-হাতুড়ি দিয়ে কবিতা বানাননি, বানিয়েছেন কলম-কাগজ দিয়েই । প্রশ্ন হল, কবিতায় মলয় কতোখানি উতরেছিলেন ? আমি তাঁর প্রথম পর্বের যে কয়েকটা কবিতা পড়েছি, চার-পাঁচটি বাদে, এখনকার কবিতার তুলনায় জোলো ঠেকেছে। 'শয়তানের মুখ' আমার কাছে নেই । ঐ বইটার সুনাম কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়ছে না । নিজের পাঠের সঙ্গে অন্যান্যদের বিশ্লেষণ মিলিয়ে বুঝেছি, মলয়ের সেই সময়কার অনেক রচনাই রুগ্ন । কবর-চিহ্ণে মুদ্রিত । দারুন চমকে দেবার মতো কবিতা তিনি লিখেছিলেন খুব কম ।
বরং তাঁর দ্বিতীয় পর্বের মেটামরফসিস আমাদের আকর্ষণ করে, কিছু-কিছু সংগঠন দারুন অভিভূত করে । এই পর্যায়ে আমরা পাচ্ছি মহাদিগন্ত প্রকাশিত 'কবিতা সংকলন' ( ১৯৮৬ ), 'মেধার বাতানুকূল ঘুঙুর' ( ১৯৮৭ ) , 'হাততালি' ( ১৯৯১ ), গ্রাফিত্তি প্রকাশিত 'মলয় রায়চৌধুরীর কবিতা' (১৯৯৪), কবিতা পাক্ষিক থেকে প্রকাশিত 'চিৎকার সমগ্র' ( ১৯৯৫ ), কবিতীর্থ প্রকাশনীর 'ছত্রখান' ( ১৯৯৫ ), আর কৌরব প্রকাশনীর 'যা লাগবে বলবেন' ( ১৯৯৬ )। এ ছাড়া স্বরচিত কবিতার দুটি ইংরেজি অনুবাদ যথাক্রমে ওয়াশিংটন স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে প্রকাশিত প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার-এর অনুবাদ 'স্টার্ক ইলেকট্রিক জেশাস ( ১৯৬৮ ) ও রাইটার্স ওয়ার্কশপ থেকে 'সেলেকটেড পোয়েমস' ( ১৯৮৯ ) । এই পর্বে অনুবাদ করেছেন অ্যালেন গিন্সবার্গের 'হাউল' ( ১৯৯৪ ) ও 'ক্যাডিশ' ( ১৯৯৫ ), ব্লাইজি সঁদরার 'ট্রান্স সাইবেরিয়ান এক্সপপেস' ( ১৯৯৭ ), উইলিয়াম ব্লেকের 'ম্যারেজ অফ হেভেন অ্যাণ্ড হেল' ( ১৯৯৮ ), ত্রিস্তান জারার 'ডাডা কবিতাগুচ্ছ' ও 'ম্যানিফেস্টো' ( ১৯৯৬ ), জাঁ ককতো'র 'ক্রুসিফিকেশান' ( ১৯৯৬ ), পল গঁগার 'আত্মজীবনী' (১৯৯৯), 'শার্ল বদল্যার' ( ১৯৯৮), 'জাঁ আর্তুর র্যাঁবো' ( ১৯৯৯ ), 'অ্যালেন গিন্সবার্গ', সালভাদর দালির 'আমার গুপ্তকথা' । 'মেধার বাতানুকূল ঘুঙুর' কাব্যগ্রন্হের কবিতাগুলি বুলেটিন আকারে প্রথমে প্রকাশিত হয়েছিল, কবিতা থাকতো মলয়ের এবং তার সঙ্গে ড্রইং থাকতো প্রকাশ কর্মকারের ।
মলয় জানিয়েছেন, কবিতা তাঁর প্রাইমারি কনসার্ন । কবিতার মধ্যেই যাকিছু দেখা ও দেখানো । ছয়ের দশকের মলয়ের চেয়ে অনেক বেশি লিখেছেন আটের-নয়ের দশকের পুনরাগত মলয় রায়চৌধুরী । এ-পর্যন্ত ( ১৯৯৯ )যা লিখেছেন, সংখ্যাগত দিক থেকে -- বয়স, অভিজ্ঞতা ও পড়াশুনার তুলনায় অনেক কম । তথাচ পূর্বাপরের সঙ্গে স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় একটা সীমারেখা এখনি গড়ে তুলতে পেরেছেন এবং বাংলা সাহিত্যের সার্থক সব কবিতার পাশে তাঁর এ-যাবৎ লেখা কবিতার একটা গণ্য অংশ অন্তত সম-বা পৃথক -মর্যাদায় গৌরবের আসন দাবি করতে পারে -- এ-মন্তব্য খুব ভেবে-চিন্তে রাখা যায় । আমার ব্যক্তিগত অনুসন্ধান জানাচ্ছে, কী কবিতায় কী গদ্যে পুনরুথ্থিত মলয় খুব ধীরে-ধীরে একটা জায়গা বানিয়ে নিচ্ছেন । এবং, তিনি অপ্রতিরোধ্য ।
বাংলা সাহিত্যে প্রথা ভেঙে যেখানে কিছুই হতে পারে না, মলয় রায়চৌধুরী সেখানে একটা মিশাল খাড়া করলেন । প্রচণ্ড স্প্যানিশ ভাবনার উদ্যত ছোবল দেখি তাঁর কবিতায় । তাঁর শব্দ খোঁজার কায়দা, শব্দ বানাবার টেকনিক, পংক্তিবিন্যাস, চিত্রকল্প-নির্মাণ ইত্যাদি পূর্বাপর কোনও কবির সঙ্গে খাপ খায় না। স্বচরিত্রে বিশিষ্ট তাঁর কবিতা । বিশেষত শব্দ দিয়েই কবিতা লেখেন তিনি, আর শব্দচয়নে তাঁর মুঠোর জোর এখন প্রায় সব মহলেই স্বীকৃত । এক-একটি শব্দ নিয়ে তাঁর দারুণ ভাবনা । পক্ষান্তরে ভাবনা বা ভাবনাসমূহের পারস্পরিক মারামারি ঢুসোঢুসি ছেঁড়াছিঁড়ি ধস্তাধস্তি থেকে বেরিয়ে আসে তাঁর শব্দ । তারপর সেই শব্দ তুলে এনে খুব ভেবেচিন্তে রয়েসয়ে তার সঙ্গিশব্দদের পাশে বসান তিনি । প্রচল ধারায় ভাষার জ্যামুক্ত তীব্র গতি বলতে যা বোঝায়, তা আনার কোনো প্রচেষ্টাই তাঁর থাকে না, হয়তো বা অপারগ ; কিন্তু একটা অন্য ধরণের স্পিড ( 'অ' গ্রন্হে তিনি বলেছেন যে 'প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার' হল স্পিডের কবিতা ), স্মার্টনেস থাকেই, যা আমাদের তাঁর কবিতা পড়িয়ে নিতে বাধ্য করে । আসলে, ঐ যে বললুম, তাঁর নতুন ও আনকা শব্দ, শব্দসংগঠন, পংক্তিনির্মাণ তথা চিত্রকল্প ফুটিয়ে তোলার কুশলতা তাজ্জব করে দেবার মতো । 'নতুন' ও 'পৃথক' বলছি তা এই কারণেও যে তিনি এ-যাবৎকাল লিখে আসছেন প্রবল অন্তর্চেতনার কবিতা, প্রচলন ধাঁচ ও লিরিকাল ব্যঞ্জনা বর্জন করে, এবং সচেতনভাবে । তাঁর সব কারবার সচেতনতা ও মেধা নিয়ে । কবিতা সম্পর্কে নিজস্ব ভাবনাচিন্তার কথা বহু দিন ধরে লিখে আসছেন মলয় রায়চৌধুরী । সেগুলো ততোটা নয়, কবিতাই তাকে করে তুলেছে বিশিষ্ট । আসলে কবিতা যা, সে নিজেই স্বক্ষেত্রে এক অপ্রতিবিধেয় শক্তি । কথাটা ভাবালুতায় আবিষ্ট ঠেকলে অন্য ভাবে বলা যায়, অহরহ একজাই অনিবার উথ্থান ও পতন, গহণ ও বর্জনের মধ্যে দিয়ে শশ্বৎ সে আরও শাক্তিশালিনী হয়ে ওঠে । পিতৃত্বের জন্য বীর্যবন্ত করে তোলে কবিকে । কবির রুচি, ইনার-কালচার, শিক্ষা, মেধা, আকাঙ্খা ও স্বপ্নের শন্নিপাত ঘটলে কবিতাই কবিকে করে তোলে প্রাতিস্বিক, নিজস্বতাময়, অনন্য । মলয়ের ক্ষেত্রে যেটা ঘটেছে, সেটা তাইই । মলয়ের প্রধান হাতিয়ার শব্দ, আর বুদ্ধি ও মেধার সহযোগে তার ব্যবহারের কুশলতাই তাঁর কবিতাকে উতরে দেয় । তথাকথিত লিরিকাল কবিদের প্যানপ্যানানির সঙ্গে তাঁর লড়াই এইখান থেকে, কিংবা জেহাদ বলুন । আজকের ঐ বয়স্ক কবিরা যাঁরা এখনও চিনিতে চিনিই ঢেলে যাচ্ছেন এবং ঢেলে যাবেন, মলয় রায়চৌধুরীর সঙ্গে তাঁদের ফারাকটা এইখানে যে, মলয়ের এতবার ম্রক্ষণ-যুতিতে নেই, চিনির সঙ্গে একটু কৃষ্ণসীস বা সীসাঞ্জন মেশানোর দিকেই তাঁর অবসক্তি । এ-ভাবে, প্রথা ভেঙেই, আজ তিনি ক্রমশ-প্রতিষ্ঠান ।
আরেকটি কথা মলয়ের কবিতা সম্পর্কে বলার আছে । সেটি হলো, তাঁর কবিতার বিষয়, বা ইমেজ বলুন আপাতত । জেনে বা না-জেনে, চেতোমান মলয় বলেছেন, কবিতায় তিনি ছুরি-চাকু চালানো রপ্ত করেছেন চার দশক ধরে। তাঁর কবিতার সেলাখানায় আছে বিবিধ তবক কারবাইন, মাস্কেট, তোপ, কর্নি, মর্টার, মলোটভ ককটেল, করপাল, বৃক্ষাদন, কুকরি, পর্শ্বধ, বাইস, ধারাবিষ আর চিয়ার-বরশার চিত্রকল্প । আর এইসব চিত্রকল্পের ধারাবাহিক অনুশীলনে তাঁকে সাহায্য করে তাঁর আশৈশব-আহরিত ইমলিতলা পাড়ার প্রায় হাজার খানেক অসৎ কুচেল অভাগা দুর্বাহৃত শব্দাবলী আর বাক্যবিন্যাস । বর্তমানের প্রতিফলনের দরুন সন্ত্রাসের ইমেজ, যা নিছক জান্তব বা যৌন নয়, এ একা মলয় রায়চৌধুরীর কবিতাতেই মেলে । যার ফলে কবির নাম না পড়েও তাঁর কবিতার স্ট্রাকচার আলাদা ও সহজ ভাবে শনাক্ত করা যায় ।
মলয় বলেছেন কবিতাই তাঁর প্রাইমারি কনসার্ন । কিন্তু নিছক কবিতা বানাতে তাঁর জন্ম নয় । বরং বাংলা গদ্যকে তাঁর অনেক কিছু দেবার আছে, দিয়েছেন, দিচ্ছেন । এই যে বিশ বছর বিরাম, তাঁর নির্জনবাস, এর ফলে তাঁর নিজের পক্ষে যেমন, বাংলা গদ্য-সাহিত্যের ক্ষেত্রেও অনেকটা ক্ষতি হয়ে গেল । মলয়ের গদ্যে যাঁরা সম্ভাবনা খুঁজে পেয়েছেন, অন্তত তাঁদের কাছে এটা অতিশয়োক্তি বলে মনে হবে না ।
বাংলা গদ্য নিয়ে মলয় রায়চৌধুরীর নিজস্ব ভাবনা আছে । বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা গদ্যের তেমন কোনো মৌলিক পরিবর্তন হয়নি । বরং বাংলা গদ্য-সাহিত্যের সূচনাকালে আমাদের জন্য যে গদ্যভাষা ধার্য করা হয়েছিল, এতো বছর ধরে ঐ গদ্যকেই মডেল হিসাবে সামনে রেখে আমরা রেওয়াজ করে আসছি । গদ্য, যা বাঙালির অভিন্ন জাতি-চিহ্ণ, তাকে উন্নত করার জন্য নিরীক্ষার কোনও আয়োজনই ব্যাপকভাবে সেরে রাখিনি আমরা । সাধু থেকে চলিত ভাষায় আসতেই আমাদের অনেকটা সময় গেছে । এখনও আমরা তৎসম শব্দের মোট বইছি আর তথাকথিত ইতরশ্রেণির শব্দগুলোকে নিজেদের অভিধানে ঢুকতে না দিয়ে বাংলা সবেধন দেড় লক্ষ নলাপচা শব্দ নিয়েই শব্দঘোঁট পাকিয়ে চলেছি । মলয় দেখেছেন, বাংলা ভাষায় শব্দ ব্যবহার, বাক্যগঠন, ক্রিয়াপদের ব্যবহার ইত্যাদি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার দারুন অবকাশ আছে । তার কিছু একটা করে দেখিয়েছেন কমলকুমার মজুমদার, কমল চক্রবর্তী, নবারুণ ভট্টাচার্য, সুবিমল বসাক এবং আরও দু'একজন নবীন লেখক। কিন্তু ব্যাপক স্তরে সেথা হচ্ছে না । নিচুতলার ভাষা ও শব্দাবলীকে মূলধারার সাহিত্যে অভিষেক ঘটাতে হবে । শুধু ভাষা ও শব্দকাঠামোকেই নয়, নিচুতলার সংস্কৃতি, জীবনযাপনের ঢঙ, আচার-আচরণ, খাওয়া-পরা, আনন্দ-দুঃখ সবই তুলে আনতে হবে । সাহিত্যের স্বার্থেই সেই ব্রাত্য করে রাখা শব্দ, ভাষা, সংস্কৃতিকে সাহিত্যে স্হান দিতে হবে, এবং তা সরাসরি । তাতে ফাঁকি রাখা চলবে না ।
বাংলা গদ্যে শৈলী, শব্দ ও ভাষার ব্যাপারে মলয়ের আকাঙ্খিত এই ভাবনার রূপকার মলয় স্বয়ং নন । তবে তিনি মনে করেন, আধুনিক বিশ্বের জন্যে একটা যুৎসই গদ্য আমাদের পেতে হবে । হয়তো তার জন্য প্রস্তুতিও সারা । দলবেঁধে মঞ্চে নামা হবে, না, যে-যার নিজের মতন করে ডেভলপ করতে করতে সেটা আনবেন তার ঠিক নেই । বুর্জোয়া শব্দভাঁড়ারকে সাবাড় করে একেবারে অব্যবহৃত নতুন শব্দের সাঁজোয়া নিয়ে তাঁর পক্ষে সম্ভব যিনি ঐ বুর্জোয়া শব্দপালকদের সমান বা তার চেয়ে বেশি প্রতিভাবান অথচ নিম্নবর্ণের বা নিম্নবর্গের ও বিত্তহীন শ্রেণির । জানোয়ারকে খতম করতে জানোয়ার হতে হয়। একমাত্র সেই নিচুতলার গাড়োয়ানই পারবেন শব্দের চাপকানি দিয়ে বুর্জোয়া গদ্যের পিলপিলে ছালটাকে উখড়ে বাংলা গদ্যে নতুন দ্যুতি ফিরিয়ে আনতে।
১৯৬২ সালে 'মার্কসবাদের উত্তরাধিকার' নামে মলয়ের যে প্রবন্ধ-পুস্তিকাটি শক্তি চট্টোপাধ্যায় প্রকাশ করেছিলেন, বা ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত 'আমার জেনারেশনের কাব্যদর্শন বা মৃত্যুমেধী শাস্ত্র' নামে জেব্রা প্রকাশনীর বইটিও, পড়ার সুযোগ আমার হয়নি । তবে ওদুটিতে গদ্যের কি কাজ ছিল তা অনুমান করতে পারি । কেননা সেই একই সময়কালে হাংরি দর্শন সংক্রান্ত মশক খানেক ইস্তাহারেই তিনি আধুনিক মনস্ক পাঠক-লেখকদের একটা অংশকে সেদিন আতপ্ত আচ্ছন্ন করে রেখেছিলেন, এ-সংবাদ আমরা শুনেছি । পরে সেই ম্যানিফেস্টোগুলোকে 'ইস্তাহার সংকলন' নাম দিয়ে মহাদিগন্ত প্রকাশনী থেকে প্রকাশ পায়, ১৯৮৫ সনে, যা আমি পড়েছি ।
পুনরুথ্থিত মলয় প্রধানত দু'ধরণের গদ্য চর্চা করে যাচ্ছেন । একটা খুবই সাদামাটা, ঝরঝরে, গতিশীল, আর মেদ বর্জিত । আন্দোলনের সময়ে লেখা বিভিন্ন ইস্তাহার, প্রবন্ধ, পরবর্তী বা আটের দশকের শেষ থেকে বিভিন্ন পত্রপত্রিকার জন্য লেখা হাংরি বিষয়ক আলোচনা, স্মৃতিচারণ, সাহিত্য বিষয়ক নিবন্ধ, ঢাকার মীজানুর রহমানের ত্রৈমাসিক পত্রিকায় প্রথমে ধারাবাহিক প্রকাশিত এবং পরে ১৯৯৪ সালে হাওয়া উনপঞ্চাশ থেকে প্রকাশিত 'হাংরি কিংবদন্তি' গ্রন্হ, হাওয়া৪৯ থেকে প্রকাশিত 'পোস্টমডার্নিজম' ( ১৯৯৫ ), এবং প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত 'পরাবাস্তববাদ' ( ১৯৯৭ ), কবিতা পাক্ষিক থেকে ১৯৯৯ সালে প্রকাশিত 'আধুনিকতার বিরুদ্ধে কথাবাত্রা', গ্রন্হগুলিতে বাহন হয়েছে এই আকর্ষণীয় ও মূল্যবান গদ্য । অন্যদিকে আর একটি গদ্য আছে মলয় রায়চৌধুরীর, যা এখনও নিরীক্ষার পর্যায়ে, যাতে অনিবার নতুন আর আপাত-জটিল শব্দের তোড়, তাকে আশ্রয় করি মলয় তাঁর এখনকার মৌলিক গল্প-উপন্যাসগুলি লিখছেন । দারুণ মডার্ন প্রোজ । দারুন-দারুন সব অ্যাঙ্গেল, যে-মুহূর্তে ক্লিক করেন, মলয় আমাদের কাছে এ-সময়ের একজন মেজর গদ্যকার হিসেবে ফুটে ওঠেন । কিন্তু ঐ, শর্ট ডিস্টান্স রানার । বেশিক্ষণ দৌড়োতে পারেন না । হেলে পড়েন । এক একটা প্যারাগ্রাফের দারুন স্পিড, কিন্তু প্যারা ফুরিয়ে যেতেই দম ফুরিয়ে আসে । আবার নতুন করে প্যারা শুরু করতে দমও নিতে হয় নতুন করে । এ-যেন ঠিক হার্ডল রেস । এটা অনুশীলনহীনতার কুফল। দেড়-দু দশকের গ্যাপ তো কম কথা নয় । সেই জন্যেই বলছিলুম, এই বিশ বছরের গ্যাপে মলয়ের খানিকটা ক্ষতিই হয়ে গেছে ।
কবিতার মতো গদ্যেও মলয় খুব শব্দ-সচেতন । কোনও-কোনও ক্ষেত্রে যেন অতিরিক্ত সচেতন । প্রায় প্রত্যেকটা শব্দেই অনেক বেশি করে কলেজা-রক্ত ঢেলে ফেললে যা হয়, নুনের পরিমাণ অনেক সময়ে লাগসই হয় না । দেখেশুনে ভাবা যেতে পারে, মলয়ের নিজস্ব একটা ঢালাই ঘর আছে । সেখানে শব্দের কিউপোলা। এক-একটা অভাগা অস্পৃশ্য দুর্ব্যবহৃত জংধরা মরচেলাগা লৌহমল বা কিট্ট নিয়ে পাঁচমিশালি গহনা বানান তিনি । হিট ট্রিটমেন্ট । কিন্তু মলয়ের, ঐ যে বললুম, সবচেয়ে বড়ো মুশকিল, এক-একটা এলিমেন্ট নিয়ে বডডো বেশি ভাবেন । হরেক কিসিমের রসায়ন, রূঢ় পদার্থ আর গ্যাস দিয়ে মূল ধাতুর খোল নলচে পালটে দেন । আবার সচেতন হয়ে উঠলেই টেম্পো খুইয়ে ফ্যালেন । দারুন মেদহীন গতিশীল গদ্যের তিনি প্রাকৃত-ভাণ্ডার । কিন্ত যেইমাত্র সচেতন হয়ে ওঠেন যে তিনি গল্প লিখছেন, সেইমাত্র একরাশ আগুন হলকা তাঁর হাত দিয়ে চাঁদির চন্দোত্তরি করে দেয় । ফলত স্ক্র্যাপ আয়রন আর স্টেনলেস হয় না । ক্র্যাক করে যায় । তিনি ভালোভাবেই জানেন, ধরো তক্তা মারো পেরেক গোছের লেখক তিনি নন । তবু মারা তিনি থামাতে পারেন না । যার ফলে পেরেকের পর পেরেক ভোঁতা হয়ে হয়ে বেঁকে-বেঁকে যায় । এর ফলে কী হয়, কোনও কোনও অনুচ্ছেদ খুব দারুন লাগলেও খুব কনট্রাইভ, আর গদ্য বানানোর দাগগুলো চোখে পড়ে যায় । এটাকে মলয়ের গদ্যের দুর্বলতা বলুন বা বৈশিষ্ট্য ।
এই অবক্ষ্যমান গদ্যেই মলয়ের 'দাফন শিল্প' পড়ি ১৯৮৪ সালে, এবং পত্রিকায়, যা পরে তাঁর প্রথম গল্পসংগ্রহ 'ভেন্নগল্প'-এর ( দিবারাত্রির কাব্য প্রকাশনী, ১৯৯৬ ) অন্যতম ভূমিকা হিসাবে পুনর্মুদ্রিত হয় । আবার সেই একই গদ্যে, সামান্য আলগা-ভাবে তাঁর প্রথম নভেলেট 'ঘোঘ' পড়ি ১৯৯২ সালে, এবং সেই গদ্যের উত্তরণ দেখি তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'ডুবজলে যেটুকু প্রশ্বাস'-এ ( ১৯৯১-১৯৯৩-তে লেখা এবং হাওয়া৪৯ প্রকাশনী কর্তৃক ১৯৯৪ সালে প্রকাশিত ) । একালের রক্তকরবীতে প্রকাশিত তাঁর সাম্প্রতিকতম উপন্যাস 'জলাঞ্জলি'ও ( ১৯৯৬ ) এই গদ্যে লেখা । 'ভেন্নগল্প' গ্রন্হে প্রকাশিত এক ডজন ছোটগল্প আর শেষোক্ত দুটি উপন্যাস পড়ে বুঝেছি, তাত্বিক মলয় রায়চৌধুরী আর লেখক মলয়ের মধ্যে একটা দারুণ প্রত্যাসত্তি রয়েছে । কিছু সর্ব-অস্তিত্বময় বর্তিষ্ণু চরিত্রকে ঘিরে লেখকের নিজস্ব চাকরিজীবন থেকে পাওয়া অভিজ্ঞতা, নানা অর্ন্তদেশীয় চেতনা আর আচার-আচরণের সঙ্গে সমকালীন রাজনীতির জটিল প্রভাব, তত্ব ও তথ্যের প্রাচুর্যের সঙ্গে বোধ ও বুদ্ধির বিচিত্র জটিলতার এক-একটি ছবি ফুটে উঠেছে এইসব গল্প-উপন্যাসে । পাতি কলকাতার কাগজগুলোতে, বিশেষত 'ডুবজলে যেটুকু প্রশ্বাস'-এর উচ্চকিত প্রশংসা পড়ে এটা ভাবা ঠিক হবে না যে বাঙালি পাঠকরা তাদের প্রোরড়মান ফেজ কাটিয়ে উঠেছে । আসলে আলোচক-পাঠকদের একটা গ্রুপ যে আক্রান্ত হয়েছেন, তার মূলে বাংলা সাহিত্যের অনেক অচ্ছুৎ-অব্যবহৃত শব্দ আর ছবি একটা বিল্টি কেটে পাঠানো হল এই প্রথম । সতীনাথ ভাদুড়িম প্রফুল্ল রায়, সুবিমল বসাককে মনে রেখেও বলা যায়, আবহমান বাংলা আখ্যান-সাহিত্যের ট্রাডিশানে যা আগে কখনও এভাবে খাপ খায়নি । মোটামুটি সবই এসেছে হিন্দি বলয় থেকে । খাস করে বিহারের দেশোয়ালি আর সড়কছাপ জংমরচে লাগা শব্দগুলোকে সামান্য ঝেড়ে-ঝুড়ে তোলা হয়েছে এই ফিকশানে । ঐ ষাট-সত্তর দশক থেকেই বিহারি বঙ্গকৃষ্টি দারুন-দারুন ঝাপট মেরে বাংলা সাহিত্যের ঘাটে এসে লাগতে আরম্ভ করেছে । একটা সফল ঝাপটা লাগল 'ডুবজলে যেটুকু প্রশ্বাস' উপন্যাসে। বিহারের আর্থ-সমাজ সংস্কৃতি-রাজনীতির এমন ভিতর-বার গুলিয়ে ফেলা ফিকশান আর কোথাওটি পাননি কলকাতার আলোচক-পাঠকরা । আর তাতেই তাঁরা দারুন অমায়িক হোসটেস হয়ে পড়েছেন 'ডুবজলে যেটুকু প্রশ্বাস'-এর। কিন্তু, এটা মলয়ও জানেন, রানওয়ে মাত্র -- উড়ান দেখব পরবর্তী ফেজে । মলয়ই দিতে পারেন সেটা । ঢাকায় 'মীজানুর রহমানের ত্রেমাসিক পত্রিকা;য় ধারাবাহিক প্রকাশিত ও গ্রন্হাকারে ১৯৯৯ সালে প্রকাশিত 'ডুবজলে'-র তৃতীয় পর্ব 'নামগন্ধ' উপন্যাসটি এখনও আসেনি কলকাতায় । 'ডুবজলে' পাঁচটি পর্বে সমাপ্য-- 'নামগন্ধ'র পর 'ঔরস' এবং 'প্রাকার-পরিখা' ।
মলয় রায়চৌধুরী বহুপ্রজ লেখক নন -- এমন ঘোষণা এখন নির্ণিমিত্ত মাত্র । খুব লিখছেন, বেশি লিখছেন । সূর্যের আলোটা কিঞ্চিৎ স্কিম করে আস্তে-আস্তে উঠে আসছে যেন । শব্দে শব্দাক্কার হয়ে সাজছে কবিতা, গদ্য । তাতে কী হচ্ছে, কতোটা, তা সময় বলবে । তাঁর সাফ কথা : "ন্যাটা হাতে যুঝে যাবো, জমিন ছাড়বো না"।
একটি ঘটনা, তা সামান্য বা অসামান্য যাই হোক না কেন, অনেক সময়ে সেই ঘটনার সাথে যুক্ত কোনও ব্যক্তিকে বিখ্যাত বা কুখ্যাত করে তোলে, যাঁর সম্পর্কে বহু সুনৃত তথ্য অনাবিষ্কৃত থেকে যায় । হাংরি আন্দোলন তেমনিই এক ঘটনা যার প্রধানতম অনুষঙ্গ হিসেবে অনিবার্য ভাবে চলে আসে মলয় রায়চৌধুরীর প্রসঙ্গ, এবং যাঁকে ঘিরে রহস্য, বিভ্রান্তি, দুষ্প্রচার, অপপ্রচারের অন্ত নেই । এটা ঘটেছে, যেহেতু ১৯৬৭-এর পরবর্তী দেড়-দুই দশকে নিজের বা নিজের প্রজন্মের অন্য কারও সম্পর্কে কোথাও কিচ্ছু লেখেননি মলয় । অথচ এই কালখণ্ডে মলয় ও হাংরি আন্দোলন নামের ঘটনা দুটি পাঁচকানে বাখান হয়ে-হয়ে এমন এক প্রবহ্ণিকার স্তরে পৌঁছে যায় যেখানে ভুল বোঝাবুঝির বিস্তর সুযোগ । আসলে আন্দোলন থিতিয়ে আসার বছর কয়েক পর থেকেই অভিবাদ-অভিশংসার এই নতুন খেলাটি শুরু হয়েছিল । লেখন জগতের একটা বিশেষ সেক্টর মেতে উঠেছিল এই খেলায় । সাহিত্যের ইতিহাসে হাংরি আন্দোলনের অবদান ব্যাপারটিকে অবজ্ঞার স্তরে পৌঁছে দেবার জোর কোশিশ চলেছিল । যার ফলে এই সময়সীমায় হাংরি আন্দোলনকারীদের নিয়ে গালগল্প দেদার হয়েছে, কিন্তু সিরিয়াস, নিরপেক্ষ ও অ্যাকাডেমিক গবেষণা একটিও হয়নি।
কেন হয়নি, তার জন্যে আমাদের আলোচক-গবেষকদের অসংবিদানকে দোষার্পণ করা সহজ, কিন্তু কেন এই অজ্ঞানতা তাও ভেবে দেখা দরকার। আমি এ-উত্তর দেব না যে ভারতবর্ষের বুকে সংঘটিততাবৎ সাহিত্যান্দোলনের মধ্যে একমাত্র হাংরি আন্দোলনের আকর্ষণ আলোচকদের কাছে এতো প্রবল হয়েছে, তার মূলে তথাকথিত অশ্লীল কবিতা বা ইশতাহার বিলির দায়ে ফুটপাতে থান ইঁট, লোহার রড সহযোগ হাংরিদের ওপর যুথবদ্ধ হামলা, পুলিশি হুজ্জত, কোর্ট কেস, জেল-জরিমানা এই সব অ্যাঙ্কর স্টোরির উপযোগী উপাদান । আসলে হাংরি আন্দোলন ছিল প্রতিষ্ঠানবিরোধী সাহিত্যধারাকে জমি পাইয়ে দেবার তাগিদে এদেশের বুকে প্রথম ও একমাত্র সামাজিক মুভমেন্ট । তার দুর্নিবার গতি সেই সময় বাংলা ও ভারতবর্ষের পাঠকদের হতচকিত করে তুলেছিল। প্রতিষ্ঠান ও প্রশাসনের কর্তারা তাকে ভয় পেয়েছিলেন, যেহেতু সাধারণ পাঠকের মনে হাংরি দর্শনের প্রতিষ্ঠা ঘটলে তাদের নিজেদের ভাবমুখে চড়ানো তাপ্পি-পুলটিশ মারা মুখোশটা উখড়ে যাবার সাধ্বস ছিল । যে-কারণে জন্মের সঙ্গে সঙ্গে আন্দোলনকে ধ্বংস করার বিরাট চক্রান্ত হয়েছিল । মিডিয়া হাউসগুলো হাংরি আন্দোলনকে এমনভাবে প্রচার করেছিল, যে সাধারণ পাঠক এটাকে নিছক হাংরি আন্দোলনকারীদের বিভীষকাময় দাপটের বহিঃপ্রকাশ বলেই ধরে নিয়েছিলেন । পুলিশি কার্যকলাপ, মামলা-মুচলেকা, জেল-জরিমানা ইত্যাদিকেও ঐ খাতে নিয়ে যাবার চেষ্টা হয়েছিল । পাঠকদের সামনে আন্দোলনের স্বরূপ ছিল অস্পষ্ট এবং বেশিরভাগ পাঠকই মনে করতে শুরু করেছিলেন যে এটা আসলে প্রতিষ্ঠান ও বুদ্ধিজীবী-বিরোধী হাঙ্গামা যার মূল লক্ষ্য অবাঞ্ছিত লেখকদের সাহিত্যক্ষেত্র থেকে বিতাড়ন আর ক্ষমতা দখল । আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে, ১৯৬৬-৬৭ সালে, হাংরি আন্দোলনকারীদের পারস্পরিক কাদাহোলি, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, অন্য কবিদের সম্পর্কে ব্যাসোহ মন্তব্য এবং হাংরি আন্দোলনকারীদের মধ্যে থেকেই এই কার্যক্রম প্রকারান্তরে সমালোচিত ও নিন্দিত হওয়ায়, পাঠকদের সংশয় আরও বহু পরিমাণে বেড়ে যায় এবং তা তাঁদের মনের মধ্যে ঘর করে যায় । পাশাপাশি সাহিত্যের ছাত্র ও গবেষকরা, যাঁরা হাংরি আন্দোলন নিয়ে লেখালিখি করেছেন, তাঁরাও থেকেছেন দ্বিধা-দ্বন্দ্বে নিমজ্জিত ।
এমতাবস্হায় নতুন করে হাংর-বিপ্লবের তাৎপর্য বিশ্লেষণ ও হাংরি-সাহিত্যের মূল্যায়নের গুরুত্ব ও প্রয়োজনের কথা অস্বীকার করা যায় না । এই বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের কয়েকটি উপায় আমাদের জানা আছে । তার মধ্যে সবচেয়ে কার্যকরী হলো, সমস্ত হাংরি রচনাবলী খুঁজে পেতে পড়া,, এক একটা লেখা ধরে চুলচেরা বিশ্লেষণ করা । এটা কিন্তু বুড়োদের দ্বারা আর সম্ভব নয় । যেহেতু তাঁরা আগেকার সব সেন্টো পড়ে ফেলেছেন এবং কনফিউজড । তাঁরা এটা করতে বসলে কনফিউজানের ঐ ফিতে দিকদারি করবে । এ-কাজ একমাত্র নতুন প্রজন্মের পাঠক গবেষকই করতে পারবেন । সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম নতুন প্রজন্মের অন্বেষকরাই ভরসা ।
হাংরি আন্দোলন ও হাংরি লেখালিখির প্রধান সুরটি অবিকৃতভাবে খুঁজে পেতে হলে আমরা আরেকটি তরিকা অবলম্বন করতে পারি, সেটা হলো সাক্ষাৎকার চর্চা । আশার কথা যে হাংরি আন্দোলনের ইতিহাস অনেক দূর অতীতে মিলিয়ে যায়নি এবং অনেকেই জীবিত । যেখানে সমীক্ষার জমঘট, সর্বোপরি বৃদ্ধ পাঠক ও গবেষকরা দ্বিধাদ্বন্দ্বে নিমজ্জিত -- সেখানে আন্দোলনের এক সময়কার শরিক, বষীয়ান লেখক-কবিদের সামনে ক্যাসেট-টেপ রেকর্ডার অন করে বসলে অন্বেষকের কাজ অনেকটা আসান হয়ে যায় । তাছাড়া সাহিত্য-বিচারের আধুনিক পদ্ধতিসমূহের মধ্যে সাক্ষাৎকার-চর্চার স্বতন্ত্র মর্যাদা আছে । গভীর অধ্যয়ন, অকপট নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে কোনও লেখকের লেখালিখি ভাবনাচিন্তা, কাজকর্ম, সমস্যা, আদর্শ, স্বপ্ন, জীবন, অপারগতা, আকাঙ্খা ইত্যাদি ব্যাপারে স্বয়ং লেখকের কাছ থেকে বিবরণ সংগ্রহের শ্রমসাধ্য কাজটি যথাযথভাবে সম্পন্ন হলে সেই বিচার-বিশ্লেষণ বা মূল্যায়নের দাম আরও বেড়ে যায় ।
মলয় রায়চৌধুরী আবার নতুন করে লেখালিখি শুরু করার পর তাঁর কাছ থেকে আদায় করা ও বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত সাক্ষাৎকারগুলি নিয়ে বর্তমান গ্রন্হটি পরিকল্পিত । বাংলাভাষায় কথাবার্তার মাধ্যমে একটি সাহিত্য আন্দোলনকে বোঝবার চেষ্টা এই প্রথম । হাংরি বিষয়ে মলয় রায়চৌধুরীর কথাবার্তা স্বভাবতই একটা দলিল । কিন্তু যেভাবে এগুলো লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তার মধ্যে দলিলের একঘেয়েমি নেই । কেননা বইটির কথা ভেবে একটা প্যাটার্ন মোতাবেক সাক্ষাৎকারগুলো নেয়া হয়নি । বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন পত্রিকাগোষ্ঠী, বিভিন্ন ব্যক্তি, বিভিন্ন অভিসন্ধি থেকে এগুলো গ্রহণ করেছেন । পক্ষান্তরে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীরা নানা মত ও পথের অপেশাদার অন্বেষকের নিজস্ব জিজ্ঞাসায় মলয় রায়চৌধুরী ও হাংরি দর্শনের প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধায় ও মমত্বে গড়ে ওঠা এই সাক্ষাৎকার সংগ্রহের মধ্যে হাংরি আন্দোলন ও বাংলা আভাঁগার্দ সাহিত্যের এই বিতর্কিত ব্যক্তিত্বকে তাঁর যাবতীয় প্রকর্ষ ও অপকর্ষসহ এই প্রথম পৌঁছে দেয়া হলো সাহিত্য গবেষকদের ব্যবচ্ছেদ-টেবিলে ।
লেখালিখি থেকে অজ্ঞাতবাসের পর সংসারধর্ম ব্যতিরেকে 'আর কিছু না করেও' হবতো-বা নিজেরই অজ্ঞাতে এক নতুন অজ্ঞাতপূর্ব পরিবেশ ও পটভূমিতে মলয় রচিত হচ্ছিলেন এই বিশ বছর ধরে । ফিরে আসার পর তাঁর লেখাত দীধিতি আমাদের অনুমানকে সপ্রমাণ করে । ছয়ের দশকের 'নিছক বুলেটিন-লেখক আর তিরিশটি কবিতার স্রষ্টা' আটের দশকে ফিরে এসে লেখকতায় দুর্দান্ত যৌবন ফিরে পান । কিন্তু এটা একরকম ভাবে সত্য, যে নিছক কবিতা বা গল্প লিখতেই তাঁর প্রত্যাবর্তন নয় । আবার কবি বলেই যে তাঁর মধ্যে কবি-কবি ভাব রয়েছে , তাও নয় । তাঁর কাছে কবিতা হলো 'আগুনের ভেতর থেকে ঝলসানো বাহুর সিগনালিঙ', এবং তিনি কবিতা শুরু করেন একটা পিক-আপ থেকে । বাসরঘরে কেলিকুঞ্চিকা পরিবৃত জামাইবাবু কবিটি তিনি নন । দারুণ বদখত, আদাড়ে, কট্টর, আর মুখফোড় এই মসীদানব । তিনি একাধারে কবি, গদ্যকার ও বক্তা । তাঁর লেখায় ও কথায় নিজের ব্যাপারে যেমন অনেক কনফেশন আছে, কোনও রাখঢাক বা পুশিদা কারসাজি নেই, তেমনি অন্যের অশালীন কুৎসিত ঘৃণ্য অসূয়াবৃত্তির বিরুদ্ধে প্রতিপ্রহার হানতেও এখন আর তিনি দ্বিধাগ্রস্ত নন । একসময় মৎসরী কলকাতার কুইসলিং বন্ধুরা অপক্রোশভাবে যে মন্তব্যটি করেছিলেন, কিছু লেখার বদলে হইচই আর হাঙ্গামার দিকেই তাঁর ঝোঁক আর চটজলদি খ্যাত পাবার লক্ষ্য, এবং তাঁর সেন্টিমেন্ট ও অপমানবোধের তোয়াক্কা না করে পর-পর দেগে গিয়েছিএন কুম্ভিলকবৃত্তি, মিথ্যাভাষণ, আত্মস্তুতি, নোংরামি আর কোরকাপের আরোপ -- সেই সব কিতবের মাথা স্লাউচ করে দিতেই যেন পুনরুথ্থিত মলয়ের প্রখ্যাপন -- "অতটা খাতির নেই যে তোমরা কশাবে এই গালে থাপ্পড় আর আমু টুক করে অন্য গাল তোমাদের হাতে ছেড়ে দেব !"
ঐ চাকু চালাবার কয়েকটা ক্যারদানি বক্ষ্যমান সাক্ষাৎকারগুলিতে মিলবে । এক-একটা তাক কতরকমভাবে করা যায়, তার নমুনাও । আসলে তিনি ফিরে এসেছেন মনের ভেতরে পুষে রাখা সেই আকাঙ্খাজ্বালা, ক্ষোভ আর বিদ্রোহকে বুকে নিয়ে । অনেক অপ্রিয় সুনৃত কথাও তিনি অকপটে লিখে আর বলে যাচ্ছেন । এবং কোনও তাগবাগ নেই, বারফট্টাই নেই । যদিবা কোনও কোনও মন্তব্যে তাঁকে ভীষণ অহংভাবাপন্ন ঠেকে, এবং কিছু-কিছু কথা প্রচণ্ড রাগ আর ঘৃণা থেকে বলার দরুণ এবং তদনুযায়ী শব্দ ব্যবহারে অনেককে খুশি নাও করতে পারেন । কিন্তু যাঁরা তাঁর লেখালিখির গতের সঙ্গে পরিচিত, যাঁরা তাঁকে চেনেন, তাঁদেরকে নতুন করে বলার কিছু নেই যে তঁর কথা ও কথনভঙ্গী তাঁর নিজের মতোই নিজস্বতাময় -- রাগি ও জেদি । লেখার মধ্যে মলয় রায়চৌধুরী নিয়ত প্রচেষ্ট থাকেন যাতে প্রতিস্পর্ধী বুর্জোয়া নিউক্লয়াসকে কামান দাগা যায়। কথার মধ্যেও সেই মারমুখি প্রবণতা । কোথাও সাংবাদিক সুলভ তীর্যক, কোথাও স্লোগানধর্মী, কোথাও চিত্রল, বক্র ও বিধ্বংসী অথচ আশ্চর্যরূপে গঠনমূলক । এটা হতে পেরেছে যেহেতু আদপে তিনি ভাষাজ্ঞানী । চিন্তাবিদ লেখক ও প্রভাবশালী বক্তা । শব্দ ব্যবহারে দারুন সচেতন । খাসা ভাষা, অকপট বর্ণনা আর সরস উপমা তাঁর রাগ-ধরানো কথাবার্তাকেও সুখপাঠ্য করে তোলে । এই সাক্ষাৎকারমালায় আমরা সেই রাগি মুখফোড় খোলামেলা তত্বজ্ঞানী, শব্দজ্ঞানী, ব্রাত্য-কথককে খুঁজে পাচ্ছি ।
মলয় রায়চৌধুরীর সাক্ষাৎকারমালার সম্পাদনার কাজ কিছুটা আকস্মিকভাবে হাতে পেয়েছিলুম । পূর্বপ্রস্তুতি প্রায় ছিলই না, মনে-মনে পরিকল্পনাও করিনি । তবে বিগত পনেরো বছরে হাংরি সিসৃক্ষা নিয়ে পড়াশোনা আর লেখালিখি করে আসছিলুম, তাতে এ যেন একটা কাজ করার গুরুত্বের কথা একেবারেই ভাবিনি তা নয় । আসলে আমি নিজেই একটা দীর্ঘ কথোপকথন চাইছিলুম এই আশ্চর্য বিতর্কিত ব্রাত্য ভাবধারার লেখকের সঙ্গে । মলয়ের সাম্প্রতিকতম গদ্যগুলি পড়ে একটা সবিমুগ্ধ শ্রদ্ধাই যেন তোড় ভাঙতে চাইছিল । দারুণ অন্য ধরণের কিছু, কিংবা একটা স্বল্পায়তন উপন্যাস লেখার কথাও ভেবেছি তাঁকে নিয়ে । মলয় রায়চৌধুরীকে নিয়ে লেখা যে কি প্রচণ্ড আত্যয়িক, তার আভাস আমি পেয়েছি । তবু নিজেকে নিরাসক্ত রাখতে পারছিলুম না । সেই মতো চিঠি চালাচালিও করেছিলুম মলয়ের সঙ্গে, তাঁর পুরোনো লেখাপত্তর, মলয় সম্পর্কে অন্যদের লেখা ঢুঁঢ়ে ঢুঁঢ়ে পড়া শুরু করেছিলুম, ক্রমে ক্রমে পরিকল্পনার একটা ভিজুয়াল সার্কলও গড়ে উঠছিল যখন, ঠিক তখনই, এক অচিরস্হায়ী ডামাডোলের মাঝে, হাতে এসে যায় এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি । তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎকারকে আমি এই গ্রন্হে অন্তর্ভুক্ত করিনি, কেননা সেগুলো প্রশ্নোত্তরের আকারে প্রকাশিত হয়নি । সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন পায়েল সিংহ ( ইলাসট্রেটেড উইকলি অফ ইনডিয়া : ১৫,৫.১৯৮৮ ) ; সোমা চট্টোপাধ্যায় ( ফ্রি প্রেস জার্নাল : ১৩.১.১৯৯১ ); এবং নওল ঘিয়ারা ( মিডডে : ১৪.৪.১৯৯১ ) । এঁদের প্রশ্নাবলী হাংরি আন্দোলনে সীমাবদ্ধ ছিল না ।
এ কথা আগেই বলেছি, এই সাক্ষাৎকারগুলি গ্রহণ করেছেন বিভিন্ন লিটল ম্যাগাজিনের সঙ্গে যুক্ত দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন অন্বেষখ, তাঁদের স্বকীয় ধারণা, নিজস্ব ভাবনা ও উদ্দেশ্য নিয়ে । সাক্ষাৎকারগুলিকে নির্দিষ্ট রীতি-পদ্ধতি ও উদ্দেশয় অনুযায়ী পরিচালনা করতে না-পারার দরুণ বা সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীদের ওপর নিয়ন্ত্রণ না-থাকার অসুবিধার ফলে, যে এলোমেলো ব্যাপারটি প্রায় অনিবার্য ছিল তাকে ডেক্সওয়র্কের মাধ্যমে, নির্বাচন ও গ্রন্হনার কাজ স্বতন্ত্রভাবে করার কথা গোড়ার দিকে মনে হয়েছিল । কিন্তু এ নিয়ে ডেলিবারেটলি নিজের সঙ্গে তর্ক করে দেখেছি, এই অসুবিধেকেই একটা মহৎ সুবিধায় পাল্টানো যেতে পারে যাতে ব্যাপারটা আরও রুচিকর আর যুক্তিগ্রাহ্য হয় । সাক্ষাৎকারগুলো পড়ে বুঝেছি, কয়েকটি সাক্ষাৎকার লিখিতভাবে নেয়া, এবং সেক্ষেত্রে স্বয়ং মলয় জবাবগুলি লিখে দিয়েছেন । মানে, এখানেও মলয়ের সেই মেদরিক্ত গতিশীল ভাষাটাকে পাচ্ছি । আবার যাঁরা মাউথপিস বা নোথখাতা ব্যবহার করেছেন, মলয়কে সামনে বসিয়ে অনর্গল কথা বলিয়ে আর লিখে গেছেন, তাঁরাও যে শুধু মলয়ের কথাগুলিকে হুবহু লিখে গেছেন, তা নয় । বরং প্রশ্ন-প্রতিপ্রশ্ন ও সেগুলির জবাবের মাঝখানে যে অন্তর্নিহিত কথাবার্তা, সেগুলিকেই সজীব করে ফুটিয়ে তুলেছেন । ফলত যেসব বিষয় গুরুগম্ভীর ছিল, সেগুলিও লেখায় অনবদ্য হয়ে উঠেছে ।
একদিকে মলয়ের সুস্পষ্ট চাঁচাছোলা সাবলীল কথাবার্তা, তার ওপর স্বচ্ছন্দ গতিতে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে পরিভ্রমণ -- তাকে লেখার আকারে ধরে রাখা অধিকতর অধিকতর বিচিত্র হয়েছে । অন্যদিকে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীরা, যাঁরা নিজের ভাষা মিশিয়ে মলয়ের কথাগুলি লিখেছেন, তাঁদের মধ্যে কোনো জড়তা বা আড়ষ্টভাব নেই বললেই চলে । সাধারণত সাক্ষাৎকার যেভাবে নেয়া হয়, অত্যন্ত মামুলি ঢঙে, তার মধ্যে উৎসাহ বেশিক্ষণ ধরে রাখা যায় না । কিন্তু এখানে খুব গূঢ় আর কঠিন বিষয়ও স্বচ্ছন্দ ভারমুক্তভাবে বলা ও লেখা হয়েছে । যেসব কথা মলয় রায়চৌধুরী এই সাক্ষাৎকারগুলিতে বলেছেন, সেগুলি আগেও নিজের স্মৃতিচারণমূলক আলোচনা ও প্রবন্ধসমূহে লিখেছেন । কিন্তু তবে, যাঁরা তাঁর মৌলিক রচনাগুলির সঙ্গে পরিচিত, তাঁরা কোনও-না-কোনও ক্ষেত্রে সাক্ষাৎকারগুলি পড়ে লাভবান হতে পারেন -- কেননা মলয়ের কথাবার্তা তাঁর লেখালিখির প্রতিনিধিত্বই শুধু করে না, তাঁর ব্যক্তিত্বের স্বাদ দেয় । তাঁর আগেকার লেখালিখি আর এইসব সাক্ষাৎকার পাশাপাশি রাখলেও বোঝা যায় তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছরে তাঁর ভাষা ও মানস কীভাবে কতোদূর বদলেছে । দোষে-গুণে ভরা একটা মানুষকে ধরবার চেষ্টা করা হয়েছে এইসব সাক্ষাৎকারে । সর্বোপরি বক্তার বলবার মুন্সিয়ানায়, লেখকদের লিপিকুশলতার গুণে এগুলি মামুলি সাক্ষাৎকারের বিবরণমাত্র না হয়ে, এক-একটি বিচিত্র তথ্যবহুল আখ্যায়িকার রূপ নিয়েছে ।
একথা বলা যাবে না যে সব কয়টা সাক্ষাৎকারই উত্তীর্ণ হয়েছে বা নূনতম মান বজায় রাখতে পেরেছে । অমুক সাক্ষাৎকারটি যে গভীরতা পেয়েছে, তার সঙ্গে তমুক পত্রিকাগোষ্ঠীর কথোপকথন নিশ্চয়ই সমান্তরাল নয় । আবার একই প্রশ্ন একই প্রসঙ্গ বার-বার ঘুরে ফিরে এসেছে বেশ কয়েকটি সাক্ষাৎকারে, সেগুলিকে কেটে-ছেঁটে লাগসই ভাবে ছাপানো যেত । কিন্তু একটি লাইনও বাদ না দিয়ে সমস্ত সাক্ষাৎকার হুবহু আসতে দিয়েছি প্রথমত আগে অন্যত্র ছেপে গেছে বলে, আর সবচেয়ে বড়ো কথা, আমি কোনও চালুনি ব্যবহারের পক্ষপাতি নই। আমার বিশ্বাস পূর্ব-প্রকাশিত কোনও রচনার ওপর সম্পাদনার নিয়ম বেশিদূর অবধাবিত হলে, রচনা ও রচকের মর্যাদাহানি হয় । সেরকম অমার্যনীয় মাস্টারিতে আমি যাইনি । খড়কুটোকে ধানের শিষের সঙ্গে আসতে দিয়েছি । তাছাড়া বেশ কিছু প্রশ্নের জবাব মলয় রায়চৌধুরী স্বয়ং লিখে দিয়েছেন বলে সেব সাক্ষাৎকারের মধ্যে ভাষাগত, শৈলীগত ও পদ্ধতিগত একরূপতাও প্রকারান্তরে এসে গেছে, এবং বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে একটি নিবদ্ধ স্তবকের মতো পরস্পর অন্বিষ্ট হয়ে উঠেছে । এদের পারস্পরিক ঘনতার সম্ভাবনা আঁচ করে কোনও যোগ বিয়োগের প্রয়োজন আমি অনুভব করিনি । পুরোপুরি যুক্তির ওপর নির্ভর করে রচনাগুলিকে পর-পর সাজিয়েছি মাত্র । সুতরাং এই গ্রন্হে যদি কিছু কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়ে থাকে, তার জন্যে আমার নয়, অন্বেষকদের অবদানই স্বীকার্য । ধন্যবাদার্হ লিটল ম্যাগাজিন গবেষণা কেন্দ্রের কর্ণধার সন্দীপ দত্ত, যিনি রচনাগুলি সংগ্রহ করে দিয়েছেন ।
পরিশেষে জরুরি যে-কথা, এবং সম্পাদক হিসেবে যে-কথা বলার দায় আমার ওপরই বর্তায়, তা হলো, সাক্ষাৎকারগুলি যাঁরা নিয়েছেন, তাঁরা মূলত লিটল ম্যাগাজিনের লোক, এবং এ-কথা অনস্বীকার্য যে বাঙালি জাতির যদি কোনও জাতীয় চরিত্র টিকে থাকে তবে ইদানিং তা বোধ করি ছোট কাগজের মাধ্যমে প্রকাশ পায় । মতান্তরে, লিটল ম্যাগাজিনগুলিকে ঘিরে যে ইন্টেলিজেনশিয়া, তা-ই আজ বাঙালির যা-কিছু । সুতরাং বড়ো মিডিয়া হাউসগুলো হাংরি আন্দোলন ব্যাপারটাকে যখন খুব করে দাবানোর চেষ্টা চালাচ্ছে, হাংরি আন্দোলনের শরিকরা পারস্পরিক কাদাহোলি করে ভুল বোঝাবুঝির বিস্তর সুযোগ করে দিচ্ছেন, তখন লিটল ম্যাগাজিনগুলি গোরস্হান খুঁড়ে হাংরি আন্দোলনকে নিয়ে নতুনভাবে ভাবাভাবি শুরু করবে, এতে আর আশ্চর্য কী ! মলয় রায়চৌধুরীর পুনরাগমনের পর এই ভাবাভাবিটা হঠাৎ রাতারাতি বিরাট আকার নিয়ে ফেলেছে । বিশেষত আটের দশকের প্রথম পাঁচ-সাত বছরে হাংরি লেখালিখির আলোচনা-পর্যালোচনার স্রোতে লিটল ম্যাগাজিনগুলির পরিমণ্ডল কিছুটা উচ্ছ্বসিত ছিল । উচ্ছ্বাস থিতিয়ে আসার পর ইদানিং হাংরি আন্দোলনকারীদের রচনার মান উৎকর্ষ ইত্যাদি নিয়ে কথাবার্তা শুরু হয়েছে, হাংরি লেখকদের প্রতি মনোযোগ বাড়ছে । এটা শুভ লক্ষণ । এই সাক্ষাৎকারগুলি ঘাঁটাঘাঁটি করার সময়েও একটা কথা আমার বার বার মনে হয়েছে, তা হলো, আধুনিক আর কম বয়সী পাঠক-গবেষকরা ব্যাপারটাকে ক্রমাগত আরও গুরুত্ব দিতে শিখছেন ।
কিন্তু মলয় রায়চৌধুরী মানে এখন আর নিছক হাংরি আন্দোলন, হাংরি বুলেটন নয়। অথচ মলয়ের সঙ্গে কথা বলতে বসেও দেখা গেছে আজকের দিনেযখন তাঁর 'কবিতা সংকলন', 'মেধার বাতানুকূল ঘুঙুর', 'হাততালি', 'ডুবজলে যেটুকু প্রশ্বাস', 'পোস্টমডার্নিজম', 'ভেন্নগল্প' 'জলাঞ্জলি', জীবনানন্দ ও নজরুল বিষয়ক প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত, বেশির ভাগ সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী মূলত দুটি বিষয় নিয়ে আলোচনা চেয়েছেন । এক, হাংরি আন্দোলনের উদ্দেশ্য কী ছিল বা হাংরি আন্দোলন শুরু হলো কী ভাবে ; আর, দুই, সাহিত্যের ইতিহাসে হাংরি আন্দোলনের স্হান কোথায় বা কতো উর্ধে । প্রশ্নদুটি এতোবার এতোভাবে তাঁকে করা হয়েছে, আর এতো ভেঙে-ভেঙে জবাব দিয়েছেন মলয় আগেও বহুবার, যে এখন আর এসব প্রশ্নের কোনো মানেই হয় না । প্রশ্নকর্তারা তো কেউ মলয় বা হাংরি আন্দোলন সম্পর্কে আগে থেকে কিছু না-জেনে বা না-পড়ে আসেননি । ধরে নেয়া যেতেই পারে যে আন্দোলনের বিদ্রোহাত্মক চেহারা, বড়ো প্রাতিষ্ঠানিক আঁতেলদের ভয় পেয়ে যাওয়া, পুলিশী পীড়ন, মারপিট, কোর্ট-কেস, জেল-জরিমানা এসব কোনও সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীকে প্রাথমিক পর্বে উদ্দীপিত করেছে, এবং তাঁরা সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন, বা প্রশ্নাবলী পাঠিয়েছেন প্রায়-হঠাৎ ভাবনা, উদ্দীপনা আর প্রশ্রয়েই । নির্দিষ্ট কোনো বিশ্লেষণ জানার আগ্রহে নয় । যার ফলে অনেকের প্রশ্ন আর মলয়ের জবাব একঘেয়েমি এনেছে । অথচ উদ্যোগ যদি আরও একটু ভাবনাচিন্তা করে নেয়া হতো, তবে তাঁরাই হয়তো ক্রমশ গড়ে তুলতে পারতেন যুগপৎ হাংরি সাহিত্য আর মলয়-সাহিত্যের আলোচনার এক নতুন সম্ভাবনা ও সার্থকতা ।
এ-কথা ঠিক যে মলয় রায়চৌধুরীর ভাবমূর্তির সঙ্গে জুড়ে রয়েছে হাংরি আন্দোলনের ইমেজ । বেশিরভাগ সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী মলয়কে ঘিরে প্রশ্নের পাহাড় গড়ে তুলেছেন, পক্ষান্তরে তাঁর হাংরি ইমেজটাকেই গ্লোরিফাই করার জন্য যেন । মানুষ মলয়কে, নিম্ন মধ্যবিত্ত থেকে মধ্যবিত্তে বেড়ে ওঠা নানান অভিজ্ঞতার আকর মলয়কে, নিজেকে সাংস্কতিক দোআঁশলা বলে পরিচিহ্ণিত করতে চাইছেন যিনি সেই মলয়কে, কবি ও গদ্যকার মলয়কে, ভাষাজ্ঞানী মলয়কে, তাত্বিক মলয়কে তাঁরা যেন খুঁজে পেতেই চাননি । আবার হাংরি প্রসঙ্গেও কিছু-কিছু প্রশ্ন এমনভাবে করা হয়েছে, তার জবাব অদীক্ষিত ও নতুন পাঠকের সামনে চিন্তাশীল কবি, বলিষ্ঠ গদ্যকার, বিরল তত্বজ্ঞানী মলয়ের আসল মানসিক গঠনটাই ধেবড়ে দিতে পারে । আবার মলয় যে ভালো বিশ্লেষক, দারুণ সমালোচক, তাঁর কাছ থেকে অন্যান্য হাংরি লেখকদের ভাষা, রচনাশৈলী, বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি সম্পর্কে বিশেষ কোনও আলোচনাই চাওয়া হয়নি । আবার মলয় সম্পর্কেই যে সবকথা জানা হয়েছে, তাও নয় । ভুলে গেলে চলবে না যে মলয় বার-বার এ-কথা বলে চলেছেন যে তিনি এখন শুধু মলয় রায়চৌধুরী হিসেবেই পরিচিত হতে চান, 'হাংরি' বা 'একদা হাংরি' হিসেবে নয় । তাঁর কবিতার বই আর গল্প-উপন্যাসের বইগুলি প্রকাশ হয়ে যাবার পরে যাঁরা তাঁর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন, তাঁদের অন্তত মলয়ের কবিতার প্রাতিস্বিক ধারা, গদ্যের ভাবনা ইত্যাদি নিয়ে প্রশ্ন করার অবকাশ ছিল । এ-ছাড়া পোস্টমডার্নিজম সম্পর্কে তাঁর কাছ থেকে বিরাট আলোচনা আদায় করা যেত। তিনি যে জায়গায় জন্মেছেন, বড়ো হয়েছেন, পড়াশোনা করেছেন, চাকরি করছেন, সারা ভারত ঘুরে-ঘুরে বেড়িয়েছেন, যার ফলে কলকাতার পাতি লেখকদের সঙ্গে তাঁর যে বৈশিষ্ট্যগত তফাৎ গোড়া থেকেই ঘটেছে, সেসব নিয়েও দারুণ আলোচনার স্কোপ ছিল ।
আরেকটি দিক থেকে মলয় রায়চৌধুরীর ওপর আলোকপাত করা দরকার । সেটা হলো তাঁর মনস্তত্বের উৎসসন্ধানের দিক । যেহেতু লেখকের মানসিকতা এক নিত্যসচল ও পরিবর্তমান জিনিস, এবং অক্ষর তাঁর বাহন, তাই কোনও একটি মানসিক অবস্হান থেকে কোনও কিছু লেখাকে লেখকের সব বলা যায় না । সাহিত্যসৃজনের ভেতর স্রষ্টার রচনার শক্তি, জ্ঞান, সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির রূপ, কল্পনা ও চিন্তাশক্তি, বিচারবোধ ও অনুভূতি বিশেষ ভূমিকা নেয় । এসবের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী হয় জীবনের প্রতি কোনও এক ধরণের দৃষ্টি আরোপ করার ক্ষমতাও। আবার এ-কথাও ঠিক যে লেখকের ব্যক্তিগত অনুভূতি, আবেগদ্বন্দ্ব, কনফিউজন, মানসিক আকাঙ্খা প্রভৃতি সব সৃষ্টিমূলক অবদানের মূলেই কোনও না কোনও ভাবে কার্যকরী । আসলে, নিছক বস্তুনির্ভর পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্টিমূলক রচনা বোধহয় সম্ভব নয় । এই সাক্ষাৎকারসমূহে মলয় রায়চৌধুরীর বুদ্ধি, পড়াশোনা, বিচারশক্তি ও দ্বন্দ্বের ক্রিয়াশীলতার রূপ ততোটা ফুটে ওঠেনি। অধচ এইসব ফুটে উঠলে সাক্ষাৎকারগুলি তখন নিছক তথ্য ও উপাদান সংগ্রহের পদ্ধতি হিসাবে গণ্য হতো না । অনেক কিছুই তখন তত্বের পর্যায়ে চলে আসতো । অনেক জরুরি প্রশ্নই সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীরা করতে পারেননি । মলয় রায়চৌধুরীকে ঘিরে প্রশ্নের পাহাড় রচনা করার অবকাশ তাই থেকে গেল।
অজিত রায়
১ বৈশাখ ১৪০৬
 অগ্নিদীপ মুখোপাধ্যায় | 27.58.255.50 | ১০ আগস্ট ২০২১ ১৯:৪২734853
অগ্নিদীপ মুখোপাধ্যায় | 27.58.255.50 | ১০ আগস্ট ২০২১ ১৯:৪২734853মলয় রায়চৌধুরীর ‘ডুবজলে যেটুকু প্রশ্বাস’ উপন্যাস
অগ্নিদীপ মুখোপাধ্যায়
লেখক দু'প্রকার। লেখক এবং সচেতন লেখক। স্বাভাবিক প্রশ্ন হল, সচেতনতাটা কী বা কোনটা। একজন সৎ ইন্সটিংকটিভ ও একজন বুদ্ধিমান মোটিভেটেড লেখক, দুজনেই পাঠকের কাছে সচেতন স্রষ্টা হিসাবে ধরা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে কি প্রাগুক্ত পার্থক্য নিরূপণ সম্ভব! আদৌ কি তার কোনো প্রয়োজন আছে ? প্রয়োজনীয়তা নাই থাকতে পারে, তবে পার্থক্য একটা থেকেই যায়। এই পার্থক্য বুঝবার সহজতম উপায় হল উভয়ের লেখা দুটি পাশাপাশি পড়ে ফেলা।
যদি কোনও লেখকের উদ্দেশ্য হয় গল্প বলা তাহলে তিনি ছোথগল্প বা পাঁচালি লিখতে পারেন। কিন্তু উপন্যাস রচয়িতার উপর দায় বর্তায়, নিছক ধারাবিবরণীর উপরে উঠে, যা তিনি লিখছেন সেটিকে চেতনা এবং দর্শনগত অভিমুখ প্রদান করা। তা যদি না হয় তবে ঔপন্যাসিক ও ডায়েরি-লেখকদের পার্থক্য করা মুশকিল।
আলোচ্য বইয়ের ক্ষেত্রে কথাগুলো বলা জরুরি হয়ে পড়ল কারণ বর্তমানে বাংলাভাষায় যে-সমস্ত এজেন্ডাহীন গদ্যরাজি উপন্যাস নাম নিয়ে চলে-ফিরে বেড়াচ্ছে তাদের প্রায় প্রত্যেককেই এই লেখার সামনে বায়বীয় বোধ হয়।এ বঙ্গে লেখক বহু। সচেতন লেখক গুটিকয়। সমালোচক হিসাবে মলয় রায়চৌধুরীকে সচেতন বলার সঙ্গে-সঙ্গেই জিম্মেদারি জন্মায় নিজের অবস্হানকে জাস্টিফাই করার। তবে তা করার আগে ডিসক্লেমার স্বরূপ বলে নেওয়া ভালো যে, গোটা আলোচনাটাই হবে গ্রন্হের প্রথম অংশ 'ডুবজলে যেটুকু প্রশ্বাস' প্রসঙ্গে। গ্রন্হভুক্ত বাকি দুটি অংশ [জলাঞ্জলি ও নামগন্ধ] পাঠককুলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হল। যে সচেতনতার কথা দিয়ে শুরু হয়েছিল, সেখান থেকেই যুক্তিজাল বিস্তৃত হোক। তবে তার আগে ছোট করে বলা থাক, যে সময় বিহার অঙ্গরাজ্য হিসাবে চরম অপশাসনে আক্রান্ত, সেই সময় একটি সরকারি আফিস, যাদের কাজ হল অচল ও পচে যাওয়া নোট চিহ্ণিতকরণ ও জ্বালিয়ে ফেলা, সেখানকার কর্মচারী ও পারিপার্শ্বিক সমাজ তথা রাজনীতিই হল এই উপন্যাসের উপকরণ।
গ্রন্হের শুরুতেই 'লেখকের কথা'য় মলয়বাবু জানাচ্ছেন, এই এপিক লেখাটির মোটিভ বা এজেন্ডা কী। এবং এই জানানো যে শুধু বলার জন্য বলা নয় তাঁ ওঁর লেখায় প্রমাণিত।লেখক বুঝেছেন যে ভারতীয় সমাজে ছাপোষা মানুষের জীবনের সারাৎসার তার আয়ুবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ উবে যেতে থাকে। এই উবে যাওয়ার বিমূর্ততাকে, শারীরিক করবার অভিপ্রায়ে, লেখক শুরুতেই বর্জন করলেন 'মেট্রপলিটান সাহিত্যরীতির' 'প্রটাগনিস্ট-কেন্দ্রিক' পুঙ্খানুপুঙ্খ চরিত্রচিত্রণ।
শুধু যে বর্জন করলেন তাই নয়, গোটা শুরুটাই যেন জাতিদাঙ্গাধ্বস্ত, আঞ্চলিক রাজনীতির সংকীর্ণতা তথা স্বার্থপরতায় বিদীর্ণ তৎকালীন বিহারের যে কোনও দিনের খবরের কাগজ। অজস্র নাম।অজস্র পাড়াভিত্তিক মারামারি, খেয়োখেয়ির ডিসপ্যাশনেট বর্ণনা।কিন্তু আবার তারই মধ্যে সূত্রের মতো ইনজেক্ট করলেন এমন কিছি ঘটনা ও চরিত্র, যেগুলোর ক্ষেত্রে লিখনশৈলীর কিঞ্চিৎ অন্যতা, সর্বাদা নায়ক-আগমন-প্রত্যাশী পাঠককে ধন্দে ফেলবে যে এরাই মূল চরিত্র নয় তো। অথবা এই ঘটনাই উপন্যাসের মোড় ঘুরিয়ে দেবে না তো।পায়াভারি ও ইন্টেলেকচুয়াল বাঙালি মধ্যবিত্তের কাছে এ সমস্ত চরিত্র অনোখা ঠেকতে পারে।তবে সকলেই এদের উপভোগ করবেন তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। সুশান্ত ও অতনু। দুটি ডায়ামেট্রিকালি বিপরীত মানুষ, যারা টানা পঁয়তাল্লিশ দিন ধরে হোটেল-রুমের দরজায়, আফিসের বড়সাহেবের প্রাত্যহিক যৌন অভিযানে কান পাততে গিয়ে আধুনিক ও চিরায়ত সংগীতের রীতিমত বোঝদার হয়ে ওঠেন। হিউগো মনটেনেগরো, বাখ, ফিল কলিন্স, বনি এম, সন্ধ্যা দ্বিজেন।প্রত্যেকদিন ভাড়া করা মহিলার সঙ্গে মৈথুনকালে বড়সাহেবের বদলে যেতে থাকা সাংগীতিক অভিরুচি এদের জীবনে এনে দেয় বিনি পয়সার মিউজিকাল এক্সট্রাভ্যাগেনজা।
শর্ট সার্ভিস কমিশনে, আর্মির চাকরি করে-আসা রাঘব, যিনি সমস্ত অফিস জুড়ে, যুদ্ধক্ষেত্রে থাকাকালীন জিপের ট্রলার থেকে শুরু করে মরুভূমিতে উটের ছায়ায় অব্দি হোমো করার ফিরিস্তি শুনিয়ে বেড়ান।
অফিস পিকনিকের ১৮ জনের দল, যারা ভাড়া করা মহিলার সঙ্গে নালান্দার ধ্বংসস্তুপে লুকোচুরি খেলেন। 'যৌনতার এই চিট ফান্ড' অবশ্য বিজয়ীকে প্রতারিত করে না। জিনি জিতবেন তিনি পাবেন দশহাজার টাকা এবং উক্ত মহিলার সঙ্গে রাত কাটানোর সুযোগ।
অফিসের উচ্চপদস্হ সেনগুপ্ত সাহেব, যিনি কলগার্লের ডিরেক্টরি সঙ্গে রাখতেন এবং যাঁর মৃত্যুতে জনৈকা সহকর্মী ফেয়ারওয়েল মন্তব্য করেন---"যৌনতা বাদ দিলে লম্পটদের চরিত্র আদারওয়াইজ ভালো হয় ।"
যদি অতিরিক্ত যৌনগন্ধে কোনো পাঠকের দম বন্ধ হয়ে আসে তবে তার জন্য রয়েছে অফিসের টেবিলে বসে ক্রমাগত হাই তুলতে গিয়ে রেটিনা ফ্র্যাকচার-করা মৌলিনাথ। তবে চরিত্র ও ঘটনাবলীর এই বিপুল ও অনুপম সমাহারকে কুর্ণিশ জানালে আরেকটি গুরুতর অভিযোগেরও উদ্ভব হয়।
অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, লেখককুল বহুবিধ ঘটনা সংবলিত উপন্যাস ভালো মতো শুরু করলেও মাঝপথে খেই হারিয়ে ফেলেন।এবং লেখার অর্গানিক গ্রোথ-এর দোহাই দিয়ে কোনওমতে লেখাটি শেষ করেন। যে কারণে বাংলাভাষায় গুণী থ্রিলার উপন্যাসের সংখ্যা হতাশাজনক ভাবে কম।
তবে মলয় রায়চৌধুরী সেই দোষও কাটিয়ে রেখেছেন। লেখার শুরুতেই বহু ঘটনার মধ্যে থেকে একটি স্বল্পবর্ণিত ঘটনাসূত্র উপন্যাসের শেষে মোক্ষমভাবে ফিরে আসে ও লেখার সামগ্রিক অবস্হান ব্যাখ্যা করে।
তখন প্রশ্ন উঠতে পারে , মানুষের জীবনের প্রতিপাদ্য যদি ক্রমশ উবে-যাওয়া হয় সেক্ষেত্রে সামগ্রিক অবস্হান ব্যাখ্যা করার দরকার কী । দরকার এই জন্যই যে উদ্বর্তন প্রক্রিয়ার একটা উলটোপিঠও রয়েছে যেটি গঠনমূলক।
বিভিন্ন জলাশয় থেকে বাষ্পীভূত জল যেমন একটি মেঘের টুকরোয় সম্মিলিত হয়, ঠিক তেমনই যুদ্ধক্ষেত্রে বাঙালিকে ফিরত আনতে চাওয়া সুশান্ত, অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ার স্বকল্পিত গ্লানি থেকে মুক্ত হতে চেয়ে কয়েকদিনের জন্য জোর করে পাগল হয়ে-যাওয়া অরিন্দম, বিহারের নিরাপত্তাহীনতায় উদ্বিগ্ন, অথচ চরম অনিরাপদ উত্তরপূর্বে নিশ্চিন্তে বসবাসকারী দুই বোন জুলি ও জুডিথ--- এই সমস্ত চরিত্রের জলাশয় থেকে তৈরি হয় সেই মেঘ, যার নাম অতনু।
ঔপনিবেশিক সাহিত্যরীতির ফিউডাল মানসিকতার নায়কনির্মাণ প্রক্রিয়াকে অস্বীকার করে লেখক তার অতনু নির্মাণ করেন সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক উপায়ে। প্রত্যেক পার্শ্বচরিত্রের সমপরিমাণ প্রতিনিধিত্ব বজায় রেখে। তাদের মৃতদেহের উপর নয়। আবার চরিত্রের নির্দিষ্ট মেয়াদ ফুরোলে, অর্থাৎ উপন্যসের শেষে, অতনুকে একগুচ্ছ বিকল্পের সামনে দাঁড় করিয়ে দেন। এ যেন মেঘের নির্দিষ্ট সময়সীমা ফুরোলে, পুনরায় জলাশয়ে জল হয়ে ঝরে পড়ার নির্দেশ। তবে অনিশ্চিত অতনু জানে না যে, সে সেখানেই ফেরত যাবে কিনা যেখান থেকে ওর জন্ম। হাওয়ায় কত মেঘই তো এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত ভেসে যায়।
লিখনশৈলীর ক্ষেত্রে উল্লেখ্য হল, এই প্রকার একটি রূঢ়, খর্খরে, ও প্রখর বাস্তবভিত্তিক উপন্যাস, যেখানে কিডন্যাপড হওয়া মেয়ের জন্য মায়ের হিন্দিতে লেখা এফ আই আরটা অব্দি চরিত্রে পর্যবসিত হয়েছে, সেখানেও লেখকের ভাষা উপমাময়, স্মার্ট এবং নির্মেদ। দাঙ্গা খুনোখুনিতে পর্যদুস্ত এক গ্রীষ্মের দুপুরের বর্ণনায় লেখক বলছেন--- 'ঘন সবুজ কচি আমের থুতনিতে হাত দিয়ে আদর করছিল একটা প্রৌঢ় আমপাতা'। সম্পাদনা প্রসঙ্গে বলার এই যে, রচনাগুলির প্রকাশকাল ডিটেলে বলার দরকার ছিল। যাঁরা অ্যাকাডেমিকালি লেখাটি নিয়ে ভাববেন তাঁদের সুবিধা হবে, কারণ লেখাটির সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক স্হানাঙ্ক রয়েছে।
আর যা না বললেই নয়, প্রচ্ছদের সঙ্গে লেখার ধাতের বিন্দুমাত্র মিল পেলেও ভালো লাগত।
( তিনটি উপন্যাস।। মলয় রায়চৌধুরী।। তেহাই প্রকাশন।। ২৫০ টাকা প্রাপ্তিস্হান: দে বুক স্টোর, কলকাতা এবং নবযুগ, ঢাকা ।। )
 অনির্বাণ মুখোপাধ্যায় | 27.58.255.50 | ১০ আগস্ট ২০২১ ১৯:৪৪734854
অনির্বাণ মুখোপাধ্যায় | 27.58.255.50 | ১০ আগস্ট ২০২১ ১৯:৪৪734854অনির্বাণ মুখোপাধ্যায় : মলয় রায়চৌধুরীর ডিটেকটিভ উপন্যাস
রহস্য কাহিনির সীমানা ছাড়িয়ে বহুদূর
স্মৃতিকাতরতা পাঠকের একচেটিয়া অধিকার নয় । লেখকও স্মৃতিকাতর হতে পারেন । কারণ লেখকও বস্তুত পাঠক । এই সহজ সত্যটিকে অনুধাবন করতে পারলে যা ঘটে তাকে বাংলা সাহিত্য খুব বেশি প্রত্যক্ষ করেছে বলে মনে হয় না । বিশেষ করে লেখক যখন তাঁর সামগ্রিক পাঠকৃতি এবং পাঠের বাইরের স্মৃতিকে ব্যবহার করছেন লিখনে, অথচ সে লিখন আত্মজৈবনিক নয়, বিশুদ্ধ রহস্যোপন্যাস, তার পাঠ অভিজ্ঞতা যে অভিনব হবেই, বলার অপেক্ষা রাখে না । মলয় রায়চৌধুরীর সাম্প্রতিকতম গ্রন্হ “অলৌকিক প্রেম ও নৃশংস হত্যার রহস্যোপন্যাস” পড়তে বসে এইসব আনকথা মনে এলোই । মলয়, যাঁর প্রাথমিক পরিচিতি হাংরি আন্দোলনের কবি হিসেবে, সে আন্দোলনের উদ্গাতা হিসেবে, যখনই গদ্যে নিজেকে এনে ফেলেছেন, পাঠকের অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির দিকে ধেয়ে গিয়েছে, সে কথাও নতুন করে বলার নয় । ‘নখদন্ত’, ‘জলাঞ্জলি’ অথবা সাম্প্রতিক সময়ের ‘অরূপ তোমার এঁটোকাঁটা’-জাতীয় উপন্যাসগুলিতে মলয় উপন্যাসের প্রথাগত আখ্যান কাঠামোকে ভেঙেছেন, কখনও একেবারে প্রতিস্পর্ধী কিছু খাড়া করেছেন । কিন্তু তাই বলে তিনি যে নিজেকে সোজাসুজি রহস্যোপন্যাসে এনে ফেলবেন, সে কথা অনুমান করতে পারেননি তাঁর অনুগত পাঠককুল ।
রহস্যপন্যাস মানে সত্যি-সত্যই ডিটেকটিভ নভেল । যাতে পষ্টাপষ্টি খুন আছে, রগরগে না হলেও, যৌনতা আছে, চক্রান্ত আছে, অতীতের সঙ্গে বর্তমানের আড়াআড়ি আছে । এ সবই এক বিশেষ সময়ের বিশেষ সাহিত্যের কথা বলে । বাংলায় পাল্প ডিটেকটিভ ফিকশনের ঐতিহ্যটি তেমন অভিজাত নয় । খুব একটা পুষ্টও নয় । তবু এ কথা অস্বীকার করা যাবে না যে, বাংলা ভাষায় এ ধরণের গোয়েন্দা কাহিনির অস্তিত্ব একটা সময়ে ছিল । স্বপনকুমার সাহিত্য তার একটা বিশিষ্ট উদাহরণ ( এ প্রসঙ্গে ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায় নামক আরেকজন লেখকের কথাও বলা যায়, যাঁর গোয়েন্দার পদবি ছিল বাজপেয়ী ) । সেসব সাহিত্যিককে মনে রেখেই কি মলয় তাঁর এই উপন্যাসের অবতারণা করেছেন ? স্মৃতিকাতরতাই কি এই রচনার মুখ্য প্রণোদন ? উত্তর খুঁজতে গেলে পাঠ করতে হয় বাংলা চটি সিরিজের ব্যানারে প্রকাশিত এই বই । যেখানে ধরতাই এক অতিবাস্তব পরিস্হিতির মধ্যে, আর ক্রমে নিয়ে যায় বাস্তবতা নামক শর্তটির কিনার বরাবর । উপন্যাসের গোড়াতেই জনৈকা মায়া পাল জনৈক নিরঞ্জনের কব্জি পাকড়ে বলছে--- ‘চলুন পালাই’ । এবং সত্যি-সত্যই ঘটছে সেই পলায়ন । কলকাতা ছেড়ে, পশ্চিমবাংলা ছেড়ে, এমনকী নিজেদের আত্মপরিচয়কে ছেড়েও পলায়ন । অন্ধ্রের এক প্রত্যন্ত অঞ্চলে আক্ষরিক অর্থেই প্রান্তবাসী মানুষের মধ্যে গিয়ে পড়ছে দুই নাগরিক মানুষ-মানুষী। শুরু হচ্ছে নাগরিক নির্মোক ত্যাগের ব্যায়াম । মায়া ও নিরঞ্জন এক বিকল্প জীবনের মধ্যে প্রবেশ করে, যাকে আধুনিকতার প্রতিস্পর্ধা বলা যায় । কিন্তু এই বিকল্প দীর্ঘস্হায়ী নয় । মায়ার রহস্যময় মৃত্যু পুনরায় নিরঞ্জনকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে নগরবৃত্তে। তার পর ? এক বাংলাবাড়িতে এক কঙ্কালের উপস্হিতি আবিষ্কার, এক কুকুরের দেহাবশেষের খোঁজ পাওয়া এবং পুলিশের এক বিতর্কিত ইন্সপেক্টর রিমা খানের সত্যানুসন্ধান ; এর পরের অংশ বলা যাবে না । গোয়েন্দাকাহিনির উপসংহার বলে পাঠকের চক্ষুশূল হতে চাই না ।
কাইনির মজা তার কথনে । মলয় সেটা জানেন মোক্ষমভাবেই । তাই রহস্যের পরত যেমন জটিল, তেমনই ল্যাবিরিন্হ এই আখ্যানের বিন্যাসেও । স্মৃতি যেমন এ-রহস্যের একটা বড় উপাদান, তেমনিই গুরুত্বপূর্ণ এই ‘স্মৃতি’ হিসেবে পরিচিত বিষয়টির সংগঠন । ইন্সপেক্টর রিমা খান কঙ্কালের আইডেনটিটি জানতে হাতড়ে বেড়ায় তার রেখে যাওয়া সিডির এক বিশাল বাঞ্চ । পর্নগ্রাফি, রকসংগীত ইত্যাদির সঙ্গে মিশে আছে কঙ্কালের আত্মজৈবনিক বিবৃতির এলোমেলো অংশ । কখনও তা যৌন অ্যাডভেঞ্চারের, কখনও তা নির্বেদ ভাবনার । আসক্তি ও অনাসক্তির লড়াইয়ে বিপর্যস্ত এক মানুষ, যে জীবনে একবারই সন্ধান পেয়েছিল পরিবর্তের । সেখান থেকে চ্যুতি যেমন তার নিজের কাছে ট্রমা, তেমনই ট্রমা তার জীবনেতিহাসের সন্মুখীন হওয়া যে কারোর । রিমার অনুসন্ধান টিপিকালি পুলিশি । এর মধ্যে কোনওভাবেই রোমাঞ্চকাহিনির ছমছমকে খুঁজে পাওয়া যাবে না । অথচ রিমার জগতে রয়েছেন ব্যোমকেশ বক্সী, ফেলু মিত্তির, পরেশ বর্মার মতো সুপার স্লথরা । এমনকী তিমির ওপরে যেমন তিমিঙ্গিল, এই সব সুপার স্লথদের উপরে রয়েছেন সুপার-সুপার স্লথ -- এরকুল পোয়ারো এবং শার্লক হোমস । হ্যাঁ, সত্যি সত্যিই এঁরা এই কাহিনির কুশীলব । এঁদের উপস্হিতি এ আখ্যানকে নিয়ে যায় স্পুফ এর পর্যায়ে । স্পুফ অথচ ছ্যাবলামি নয় । ‘ডার্টি ফেয়ারি’ রিমা খান, তার নিজস্ব ট্রমা, তার ব্যক্তিগত চ্যালেঞ্জসহ কখন পাঠকের ঘাড়ে এসে নিঃশ্বাস ফ্যালে, টের পাওয়া যায় না । এক বিভ্রম তৈরি হয় । ডিতেকটিভ কাহিনিই পড়ছি তো ! সর্বতোভাবে বিচ্ছিন্ন মানুষের সংকট, যৌনতার ধূসর-ধূসরতর তরঙ্গভঙ্গ এবং এক সাবলাইম প্রতিশোধের মাথা চাড়া দেওয়া -- এ কি কোনও মামুলি থ্রিলার ? পরক্ষণেই মনে হয় এ বিভ্রমমাত্র, আসল অভিপ্রায় তো রহস্যের উন্মোচন । ডিটেকটিভ কাহিনির পোড়-খাওয়া পাঠক জানেন, রহস্যের সমাধান হবেই । সেই অনিবার্য সমাধানবিন্দুতে যাওয়ার আগে যে রোমাঞ্চকুণ্ডলিতে পাক খাওয়া, তা-ই এই ধরণের কাহিনির মূল মজা । সে পাক মলয় যুৎসই ভাবেই খাইয়েছেন । কিন্তু সেই গোলকধাঁধা নির্জস খুন আর ডিটেকশনের নয় । তাতে মিশে আছে অস্তিত্ব নামক একটা অতি প্রাচীন বিষয়ের একান্ত সমস্যাও, যা তাঁর পূর্ববর্তী লিখন ‘জলাঞ্জলি’ এবং ‘নখদন্ত’তেও ছিল, প্রকাটভাবে ছিল ‘অরূপ তোমার এঁটোকাঁটা’য় । এদিক থেকে দেখলে মলয় সরে আসেননি তাঁর অভ্যাসগত লিখন থেকে । মলয়ের সঙ্গে সহবাসরত পাঠকের তাই কোনও ভয় নেই এই ‘নতুন’ উপন্যাসে । বরং প্রাপ্তিযোগ অনেক ।
একটা কথা শেষমেশ বলতেই হয় । এই বই লিখে মলয় একটি ঘোরঘট্ট কাণ্ড ঘটিয়ে ফেললেন নিঃশব্দে। বাংলা রহস্যকাহিনির বাজার যখন তলানিতে এসে ঠেকেছে, তখন এমন এক মেধাবী লিখন সত্যিই আশার সঞ্চার করে । উদ্বেগ জাগে পরবর্তী রিমা খান অ্যাডভেঞ্চারের জন্য । আরও কি লিখবেন মলয় ? এই সময়ের রহস্যকাহিনি লেখার জন্য যে পাঞ্জার তাকতের প্রয়োজন, তা যে তাঁর রয়েছে, তা প্রমাণিত । একন দেখার, সিরিজ কনটিনিউ করার মানসিকতাটি তিনি লালন করছেন কিনা তা দেখার । পাঠকের শুভেচ্ছা রইল মলয়ের জন্য । আরও শুভেচ্ছা রইল ‘ডার্টি ফেয়ারি’ রিমা খানের জন্য । বাংলা সাহিত্যে এমন এক নারীকে আগে দেখেছি কি ? মনে তো পড়েনা ।
 অনুপম মুখোপাধ্যায় | 27.58.255.50 | ১০ আগস্ট ২০২১ ১৯:৪৭734855
অনুপম মুখোপাধ্যায় | 27.58.255.50 | ১০ আগস্ট ২০২১ ১৯:৪৭734855অনুপম মুখোপাধ্যায় : মলয় রায়চৌধুরীর ‘জখম’
জখম : একটা সেতু : পেছনে আকাশ । সামনে আকাশ । যে দিকে চোখ যায় কিছুটা হলেও আকাশ । আকাশ । লাল । লাল হতে পারে সূর্যের আগামি মৃত্যুর জন্য । হতে পারে আগ্নেয়গিরির লাভা বমনের অসংযমের জন্য । সেহেতু একটা লোক । লোকটা কি মলয় ? মলয়ের রঙ কি হলুদ ? তাঁর মুখে কি নরম হয়ে আসা ডিমের আদল আছে ? হতে পারেন লোকটা মলয় !দু-হাতে কান চাপা দিয়েছে লোকটা । মুখে তার মমির মতো আতঙ্কিত বিস্ময় । বিস্মিত আতঙ্ক । আমাদের আতঙ্ক । মুখ তার চিরকালের মতো হাঁ হয়ে গেছে । চোখ বিস্ফারিত — চিরবিসজফোরণেই হয়তো । আমাদের বিস্ময় । মমির মুখে যে বিস্ময় গলে যাওয়ার অপেক্ষায় থাকে । হয়তো কোনো ভ্রুণের মমি — মাতৃগর্ভেও আতঙ্কেই যে ফাঁকা হয়ে গেছে ওই আকাশ মাতৃজঠরের চামড়া । সেতুটি । অস্তিত্বের মধ্যে । জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত । প্রথম জন্ম থেকে প্রথম মৃত্যু পর্যন্ত । অসেতুসম্ভব তবু নয়ই বা কেন ? পেছনে কিছু অস্পষ্ট মূর্তি । ছায়ামূর্তি বলব না তাদের । তারা কি মলয়ের পেছনে ? তারা কি আসছে ? না চলে যাচ্ছে ? ওরা কি কারও স্বজন হতে পারে ? বিশ্বচরাচরে ছুটে চলেছে যে আর্তনাদ — মলয় কি তাকে কিছু বাড়ালেন ? বাড়াতে কি পারে কেউ ? ‘জখম’ পড়ে আমার মনে হয়েছে, এই দীর্ঘ কবিতার প্রণেতা একজন চিরশিশু । বড়ো হওয়ার কোনো ইচ্ছে তাঁর নেই । ইনোসেন্সের বাইরে গিয়ে সেই ক্ষমতাও তাঁর নেই । ইনোসেন্ট না হলে কে চায় কবিতাকে বদলে দিতে ? মানুষকে সুন্দরকে দেখার চোখ বদলে দিতে ? অসম্ভব শৈশব, অবিশ্বাস্য কান্না বুকে না জমিয়ে এই কাজে নামা যায় না, যাবে না । ‘জখম’ খুব স্পষ্টভাবে মলয় রায়চৌধুরীর মনের নৌকোয় বিশৃঙ্খলাকে তুলে আনে । একই সঙ্গে যন্ত্রণা ও আনন্দ, আশা এবং হতাশা । এক বিশ্বজনীন কম্পোজিশন । এক ম্যানিফেস্ট — যে কোনো রকম মনের, যে মনে আঁচড় কাটছে যাতনা ও উদ্বেগ । কেন ‘আধুনিক’ বললাম, ‘অধুনান্তিক’ বললাম না ? ‘জখম’-এর প্রতিটি রঙ ও রঙহীনতা, আকার ও আকারহীনতা ক্লস্ট্রোফোবিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ করতে চায় । মোকাবিলা করতে চায় অ্যাংস্টের সঙ্গে —
ওফ
আমার ভালোলাগছে না এইসব
আমি মরে যাব আমি মরে যাব আমি মরে যাব
আমার দুঃখকষ্ট বুঝতে না পেরে ভেতরে ভেতরে আমার হাড়গোড় চিড় খেয়ে যাচ্ছে
খারাপভাবে জড়ো করা গা-গতর দিয়ে তৈরি হয়েছে আমার দেহাভিমান
সমস্ত বারণ আমান্য কোরে আমি আমার আত্মার কাছে যেতে চাইছি
উপরের উদ্ধার থেকেই বলছি ‘জখম’-এর পরিস্হিতিকে আধুনিক বলা সঙ্গত । মলয় এখানে তাঁর আধুনিকতায় হাঁপিয়ে উঠেছেন । ছটফট করছেন, শারীরিকতায় যেতে চাইছেন আত্মার কাছে । আমি বলতে চাইব চেতনা থেকে চৈতন্যের দিকে । অধুনান্তিকের দিকে । বোদলেয়ার থেকে গিন্সবার্গে নয়, রামপ্রসাদে । ‘জখম’ অধুনান্তিক নয়, কারণ এখানে জার্নির শুরুয়াত আছে — মানচিত্র চিনে নেয়া আছে — রাস্তার হালহদিশ জেনে নেওয়ার প্রমাণ আছে — জার্নিটা নেই । আধুনিকতার মৃত্যুর নিশ্চয়তা আছে — পোস্টমর্টেমের বর্ণনা আছে — মৃতদেহটা উধাও হয়নি, বাতাসের পচা গন্ধে তার প্রমাণ । অবশ্য অধুনান্তিকের জন্মের আগে তারা আকাশে ফুটে উঠেছে — সেটাই রাস্তা চেনাচ্ছে মলয়কে । তিনি লিখছেন :
এখন আমি প্রত্যেকটা ব্যাপারের শব্দ শুনতে পাচ্ছি
আমি আমার নিজের পাশে শুয়ে নিজেকে ভালোবাসলুম
উলিয়াম ব্লেকের সঙ্গে শুয়ে রইলুম তার আঙুরমাচানের নিচে
হুইটম্যানের চটের ওপর শুয়ে মৌচাক থেকে বাড়তি মধু ঝরে পড়ার গম্ভীর শব্দ শুনলুম
নীলার লেপের নিচে শুয়ে আদ্দেক রাত্তিরে উঠে এলুম নিজের ঠাণ্ডা বিছানায়
জীবনানন্দের বিছানার খোঁজে
‘জখম’-এর কবির স্বজন এঁরাই । এঁরা — আধুনিকতার মধ্যেই এঁরা ছিলেন, কিন্তু কদাচ তার সীমার ধারণায় এঁরা আঁটেননি । এঁদের মধ্যেও আমরা ক্লস্ট্রোফোবিয়ার সঙ্গে লড়াই এবং চৈতন্যের ছোঁয়ায় অ্যাংস্ট থেকে সোনার ফসল ফলাতে দেখি । বোদলেয়ার এঁদের সঙ্গে একই পংক্তিতে খেতে বসতেন না । যতই স্বর্গের স্বপ্ন দেখুন, আতঙ্কের স্বর্গ ছোঁয়া হয়নি তাঁর ।
আই আতঙ্ক আধুনিকতার আমদানি । সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার, ছুটে চলার ধারণা ও আকাঙ্খাই এর জন্ক-জননী । প্রকৃতির উপরে মানুষের জয়লাভ সম্ভব — এই অবাস্তবতা এর পৃষ্ঠপোষখ । মানুষের আবহমান অর্জনের বিরুদ্ধে বিজ্ঞান কথা বলতে চাইল — কিছু সংখ্যালঘু মানুষের দৌলতে এই স্পর্ধাও দেখা দিতে পারল । উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে বোদলেয়ার অবক্ষয়ী আধুনিকতার অবতার হয়ে উঠলেন । তাঁর মুভমেন্ট শেষ পর্যন্ত নাম নিল The Decadence । এই নাম থেকেই বোঝা যেতে পারে চরিত্র । এই সাহিত্যের উপাদানগুলোকে মিলিয়ে নেওয়া যায় শেষ তিনটে খ্রিস্টপূর্ব শতাব্দীতে রচিত গ্রিক সাহিত্যের সঙ্গে, বা সম্রাট অগাস্টাসের মৃত্যুর ( ১৪ খ্রিস্টাব্দ ) পরে রচিত রোমান সাহিত্যের সঙ্গেও । এমন একটা সভ্যতা — যে তার সঙ্গে সূক্ষ্ম মূল্যবোধ এবং সৌন্দর্যবোধকে আঁকড়ে থাকলেও বোঝা যাচ্ছে সেরা সময়টা পেরিয়ে এসেছে, এবং ক্ষয়জনিত মধুর স্বাদ ছড়িয়ে দিচ্ছে অতিপক্ক ফলের মতো ।
বোদলেয়ারের কাছাকাছি সময়ে ফ্রান্স এবং বৃহত্তর ইউরোপের সভ্যতারও একই হাল হয়েছিল । বোদলেয়ারের Les Fleurs du Mal প্রকৃতি এবং প্রাকৃতিকের যে কোনো শর্তেও বিপ্রতীপে শিল্পসাহিত্যকে বসাতে চাইল । বসাতে চাইল নীতি এবং যৌনতার বিপ্রতীপে । শিল্পসাইত্যকে বলতে চাইল — একজন শিল্পী কেবলমাত্র তার স্টাইলকে উন্নত করে যাবেন, জৈবিক প্রবৃত্তিগুলোকে কোনো স্হান দেবেন না । অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ওপর পোশাক চাপিয়ে দিতে হবে । প্রাকৃতিক লাবণ্যের ওপর রঙ । মানবিক অভিজ্ঞাতার বাইরে যাওয়ার জন্য ড্রাগ নেবেন, যৌনতা নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট চালাবেন । র্যাঁবো যেমন বলেছিলেন — The systematic derangement of all senses.
ওই সময়ের চরিত্রে ছিল অবসাদ, একঘেয়েমি, মানসিক অস্হিরতা এবং শক্তিহীনতা । সেই রাস্তাতেই দেখা দিল বিংশ শতাব্দীর সূচনা । লক্ষণগুলো থেকেই গেল ।
সেই The Decadence ছিল সুররিয়ালিজমের পূর্বপথিক । আঁদ্রে ব্রেতোঁ ১৯২৪ সালে Manifesto of Surrealism দ্বারা সুররিয়ালিজমের সূত্রপাত করলেন । স্বাধীন ও মুক্ত সৃজনশীলতার ওপরে যে কোনো বন্ধনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষিত হল । বলাই যায়, The Decadence না আসলে সুররিয়ালিজম হয়তো দেখা দিত না । সুররিয়ালিজম উড়িয়ে দিল যুক্তি, প্রতিষ্ঠিত নীতি, সমাজ ও শিল্পের যে কোনো প্রথা, এবং শিল্পপদ্ধতির ওপরে কোনোরকম পূর্বধারণা ও উদ্দেশ্যের শাসন । মনের নির্জন স্তর, অবচেতন স্তরকে বাধাহীন কাজ করতে দেওয়া হল । বলা হল এটিই জ্ঞানের একমাত্র উৎস । সুররিয়াল কবি-শিল্পীরা অটোমেটিক রাইটিং-এর দিকে চলে গেলেন । স্বপ্নের উপাদানগুলোকে কাজে লাগালেন । থাকতে চাইলেন তন্দ্রা ও জাগরণের মধ্যবর্তী স্তরে । সৃজন করলেন প্রাকৃতিক অথবা কৃত্রিম বিভ্রম । দিকপালরা হলেন আঁদ্রে ব্রেতোঁ, লুই আরাগঁ, সালভাদর দালি ।
শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে সুররিয়ালিজমের চেয়ে বড়ো কোনো মুভমেন্ট বিংশ শতাব্দীতে আসেনি । অধিকাংশ শিল্পকর্মে সাহিত্যে এর প্রভাব আছে । আমাদের দেশে জীবনানন্দ দাশ এর প্রভাব স্বীকার করেছেন তাঁর কবিতায় । এই ২০১৩ সালেও অনেকের লেখায় এর ছোঁয়া আছে । যে কোনো কবিতাপত্রেই চোখে পড়ছে । এই ধরণের টেক্সট সহজে জনপ্রিয়ও হয় ।
‘আমি’ — এই ‘আমি’কে নিয়ে জলঘোলা কিছু কম হয়নি, হয় না । পোস্টমডার্নরা ‘আমি’ নিয়ে সংকোচে থাকেন । ‘নতুন কবিতা’ নিয়ে যারা কথা বলছেন, তারাও । কিন্তু ঘটনা হল ‘আমি’-র সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিসরের সেভাবে কোনো যোগ থাকতেই হবে এমন কোনো কথা নেই । ‘আমি’ হয়ে উঠতে পারে বিশ্বজনীন আমি — আর সেখানেই হয়তো চ্যালেঞ্জ । ঘটনা হল ‘আমি’র বাইরে কোনো পৃথিবী হয় না । নিজেকে জানাই জানার শেষ উচ্চারণ — অন্তত সেই কথা ও কাহিনী । নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া — এক জীবন যথেষ্ট নয় তার জন্য । ‘আমি’কে অবলম্বন করে ধ্যান করলে ক্রমে আর অজ্ঞাতকে অনতিক্রম্য মনে হয় না, তার সঙ্গে মিশে যাওয়াও সম্ভবপর মনে হয় । আমি এক অবলম্বনও হয়ে উঠতে পারে ( যেমন বিগ্রহ ), মুখ লোকোনোর আড়াল নয় ( যেমন সুনীলের ‘আমি’ ) ।
সংক্যা কি একটা ফ্যালাসি বলা যায় ‘জখম’এর টেক্সটে ? কিছু উদাহরণ :
৪৫০০০ ডানহাত, ১৩৫ জোড়া পা, ১৯৬৫ মডেল
২৭৬০ লক্ষ টাকার মানিঅর্ডারফর্ম, ৬৮০০০ প্রচারপত্র,
৪৯ জোড়া আরামখেকো লাশ, ৫.৩৮ ডি.সে. শীত,
১ জোড়া জংলি হাঁস, ৪০০০ লোক, ২০০০ কঙ্কাল,
৫০০ লিটার রাজনীতি, ৩৫০০০০ আমলা, ২৫০০০ আঁত
এখানে ৪০০০ অনায়াসে ৪৫ হতে পারত, ২৫০০০ হতে পারত ২৫০ । অনেকে হয়তো একে কবির খেয়াল বলবেন । খেয়াল হলেই বা কী যায় আসে ? কবির খেয়াল না থাকলে কার থাকবে ? তাছাড়া আরেকটা ব্যাপার আছে । সেটা যুক্তির ব্যাপার । ‘কেন’-র বাইরে বেরিয়ে যাওয়া । অতিকথন । লাগাম ফেলে দিয়ে । সুররিয়াল অবশ্যই । দালি যেমন মানবদেহের কোনো একটা অঙ্গকে অসদ্ভাবের দিকে বাড়িয়ে দিতেন । সেই অঙ্গ লেনিনের হলেও ।
প্রতীকের ব্যবহার একটা প্রসঙ্গ । ‘আমি’ নিজেই একটা প্রতীক । তাঁর শরীর, তাঁর শরীরচেতনা — প্রতীক । প্রকৃতি-প্রতীক । প্রাকৃতিক উপাদানসমূহ — প্রতীক । সৌন্দর্য — প্রতীক । সমাজচেতনা — প্রতীক । সমগ্র কবিতাটিকেই আমরা অর্থময়তার দিকে না তাকিয়েই, কেউ কবিতাটিকেই আমরা অর্থময়তার বহুস্তরিকতাকে বারবার ছুঁতে ও অতিক্রম করতে দেখি । অবশ্য প্রতিকী তাৎপর্যের দিকে না তাকিয়েই, কেউ কবিতাটি অনায়াসে পড়তে পারেন । কোনো হানি তাতে হবে না । পোস্টমডার্ন পরিসরেও ‘জখম’ তাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি টেক্সট । শিবলিঙ্গ তো শিবের যৌনাঙ্গ — এটাই তো যথেষ্ট । সেখানে পুরো শিবকে পাওয়া যাবে কিনা — এই চিন্তায় ফল কী ? কয়েকটি পংক্তি :-
১. বোবা গাছ থেকে অক্সিজেন পাওয়া যাচ্ছে বাজারদরের চেয়ে অনেক সস্তায়
২. কেন পৃথিবীর মাটিতে আপেল নেমে আসে আমি জানলুম না
৩. অবলা ভিতু জাহাজকে বাঁচাতে লাইটহাউস
৪. নিজেরি চিঠি নিয়ে নিজের বাড়ি খুঁজে পাচ্ছে না ডাকপিওন
৫. মেঘের নিচে নিচে নেমে যায় ১২০০ মাইল ভ্রাম্যমান ছায়া
উক্ত পঙক্তিগুলোতে প্রতীক আছে । আবার যিনি চান না, তাঁর জন্য নেই । জোর গলায় বলা চলে — নেই, কারণ কোথাও কোনো দাগ নড়েচড়ে উঠছে না, যা চিরাচরিত প্রথা অনুসারে কবিতাটিতে টিকতে পারবে । যখন মলয় লেখেন —
৮০০০০০ উদ্বোধনকারী মন্ত্রী ও তাদের কাঁচিদঙ্গল
প্রাচীন মায়াপুর থেকে উড়ো খামে চলে আসে
আমরা আর প্রতীকের ধারণার সঙ্গে ঠিকঠাক এঁটে উঠতে পারছি না । যখন বলেন —
ঘুম থেকে উঠে দেখছি সারা শরীর ছড়ে গেছে
আমাদের আর প্রতীকের দরকার মনে হয় না । শিবলিঙ্গে যে মেয়েরা জল ঢালতে যায়, তারা লিঙ্গ মনে রাখলেও সেটা শিবের নয়, হতে পারে বয়ফ্রেণ্ডের । শিবকেও মনে রাখে কি ?
মলয়ের সমাজচেতনা নিয়ে হয়তো অনেক বাকবিস্তার করা যায় । কিন্তু একটা কথা ভুললে চলবে না — কবির নিজের বাইরে কোনো সমাজ হয় না । এমন কোনো কবিতা আজও প্রকাশিত হয়নি যা সামাজিক নয় । এমন কোনো টেক্সট হয় না । কবি একজন মানুষ । মানুষ একটি সামাজিক প্রাণী । একজন মানুষের ভাব বা ভাবনা হয়তো সমাজের তোয়াক্কা না-ও করতে পারে — অন্য হোমো স্যাপিয়েনরা পড়বে বলেই করলেন । একটি প্রকাশিত টেক্সট সামাজিক না হয়ে পারে না । ‘নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ’ও একটি সামাজিক টেক্সট । ‘সারদামঙ্গল’ও তাই । আর সমাজচেতনা ? সমাজের ফোটোগ্রাফ কি সমাজচেতনার দলিল ? মোটেই না । তাহলে তো দোকানের হিসেব খাতাই চমৎকার সামাজিক কবিতা হয়ে যেত । আর ‘ফাউস্ট’ হয়ে যেত অসমাজিক টেক্সট ।
আমার মনে হয় সমাজসচেতন টেক্সট অর্থে যেখানে কবি বা শিল্পী তাঁর মনের ঘরে আনাগোনা, আদানপ্রদান, লেনদেনগুলোকে স্রোতায়িত করেছেন । সেটা স্ট্যাটিক হলেও হতে পারে — যেমন স্বদেশ সেনের কবিতা ) গমন থাকলেও তোলপাড় নেই ) । কাইনেটিক — যেমন ‘জখম’ । কিছু পঙক্তি যেখানে মলয় একজন সমাজসচেতন কবি —
১. আমার শরীরে এখন চোলছে কেপমারি খুনজখম রাহাজানি ছিনতাই/আমার হাত-পা দিয়েই আমাকে সকলে মিলে পেটাচ্ছে
২. স্ত্রীলোকের চেয়ে য়ুরেনিয়াম আজকাল বেশি দরে বিকোয়
৩. ভারতবর্ষের ১০৮ দিকে আমি নিস্তারহীন নজর রাখছি খারাপ মানে খারাপ কিনা জেনে নিতে
আসলে কবির সমাজচেতনা একটা মিথ । যে কোনো কবি, যে কোনো টেক্সট সমাজসচেতন । শুধু যে টেক্সট মৌলিক নয় — সেটা ছাড়া । ‘জখম’কে অনুসরণ করে রচিত টেক্সট সামাজিক হলেও সমাজসচেতন আমরা তাকে বলতে পারি না । সমাজে তারও অবস্হান থাকবে, যেমন মানবদেহে টিউমার আমরা । ‘জখম’কে অনুসরণ করা অসম্ভব হলেও সেই চেষ্টার উদাহরণ বাংলা কবিতায় কিন্তু আছে ।
একটা প্রসঙ্গে এই সুযোগে চলে আসা যায় । এর আগে কেউ হয়তো এই প্রসঙ্গে কথা বলেননি । ‘জখম’-এর কিছু পঙক্তি আমাকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কিছু কাব্যগ্রন্হেও কিছু পঙক্তির কাছে নিয়ে যায় । মিল খুঁজে পাই আমি । কিছু উদাহরণ দিচ্ছি —
মলয়–আমার খানিকটা দেরি হয়ে যায়, জোতোয় পেরেক ছিল
মলয়–স্ত্রীলোকদের পায়ে-চলা রাস্তার গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে আমি এগিয়ে যাচ্ছি তাদের অ্যামেচার আস্তানার দিকে
সুনীল–অন্ধকারে স্ত্রিলোদের মধ্যে ডুব দিয়ে দেখেছি দেশলাই জ্বেলে
মলয়–নিজের সই জাল করে চালিয়ে দিলুম গোটা শীতকাল
সুনীল–বেয়ারা পাঠিয়ে কারা টাকা তোলে ব্যাঙ্ক থেকে ? আমি তো নিজের সইটা এখনও চিনি না
মলয়–আমি অন্ধ ভিকিরির হাত থেকে ৫ পয়সার চাকতি তুলেনিয়েছিলুম/আমি খইয়ের ভেতর থেকে কাড়াকাড়ি কোরে ছিনিয়ে নিয়েছি মড়ার দয়ালু পয়সা
সুনীল–আমি ফুলের পাশে ফুল হয়ে ফুটে দেখেছি, তাকে ভালোবাসতে পারি না ।/আমি কপাল থেকে ঘামের মতন মুছে নিয়েছি পিতামহের নাম/আমি শ্মশানে গিয়ে মরে যাবার বদলে, মাইরি, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম ।
মলয়–আহ এ ভুল কোল্কাতা এ ভুল মানুষমানুষী
সুনীল–কলকাতা আমার বুকে বিষম পাথর হয়ে আছে/আমি এর সর্বনাশ করে যাবো–
আমরা ধরে নেব সুনীল-গিন্সবার্গ-মলয় : এই ত্রিভূজ নিয়ে অনেক বলা বাকি আছে বাংলা কবিতায় । এখানে হয়তো সন-তারিখ কাজে আসবে আমাদের ।
বাংলা ভাষা এবং যেকোনো ভাষায় লিখিত চিরস্মরণীয় দীর্ঘ কবিতাগুলির একটি হল মলয়ের ‘জখম’ । এর সম্পর্কে কথা না বলে বাংলা কবিতার কোনো আলোচনা পূর্ণ হতে পারে না । অবশ্যই একটি আধুনিক টেক্সট । কিন্তু বাংলায় শেষ আধুনিক কবিতা হিসেবেই আমরা ‘জখম’কে গ্রহণ করব । এর পর বাংলা কবিতার আধুনিকতা সম্পৃক্ত হয়ে গেছে, এবং তলানি জমতে শুরু করেছে । এখনও জমে চলেছে ।
এটা খুব ভালো লক্ষণ যে, চিরকাল উপেক্ষা করে এসে অবশেষে বাংলা সাহিত্যজগত মলয় রায়চৌধুরীর ওপর আলো ফেলতে শুরু করেছে । এখনও আলো না হলে আগুন ধরে যেতে পারে — এই আশঙ্কাতেই কি !
(‘স্বপ্ন’ পত্রিকার মলয় রায়চৌধুরী সংখ্যায় প্রকাশিত । শরৎ ২০০৮, বাংলা ১৪১৫ । নবীনচন্দ্র কলেজ, বদরপুর, আসাম ৭৮৮ ৮০৬ )
 প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায় | 27.58.255.50 | ১০ আগস্ট ২০২১ ১৯:৪৯734856
প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায় | 27.58.255.50 | ১০ আগস্ট ২০২১ ১৯:৪৯734856প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায় : হাংরি আন্দোলনের স্রষ্টা মলয় রায়চৌধুরী
ছয়ের দশক । নেহেরুর দ্বিতীয় যোজনা অনেকটা সরে গেছে বোম্বাই মডেলের দিকে । ঔপনিবেশিক খেসারত দিতে ভারত-চিন যুদ্ধ । ভারত পাকিস্তন যুদ্ধ । স্বদেশি আন্দোলনের সময়ে জাতীয়তাবাদী নেতারা যে সুখি, সমৃদ্ধ, উন্নত ভারতবর্ষের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন, উত্তরঔপনিবেশিক ভারতে তা সেই সেময় দিশা হারিয়েছে । বাংলা সাহিত্যে তখন মূল ধারা দুটি । একটি বুদ্ধদেব বসু, আলোক সরকার, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, বিষ্ণু দে, সমর সেন, কবিতা সিংহ, শতভিষা নামক পত্রিকাসহ খ্যাতির মধ্যগগনে । অন্য ধারাটি বামপন্হী সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মঙ্গলাচরণ, রাম বসু প্রমুখরা । এই সময়কালে সাহিত্যের অঙ্গনে আবির্ভাব হলো হাংরি আন্দোলনকারীদের । যা খাপ খোলা তলোয়ার নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল, নেতৃত্ব দিলেন মলয় রায়চৌধুরী নামের একুশ বছরের যুবক । কলকাতা শহরের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাবুরা ইস্তাহার দেখেছে ট্রেড ইউনিয়ান আন্দোলনে, রাজনৈতিক দলে । তা বলে সাহিত্য আন্দোলনে ইস্তাহার বিলি করে ! ভাবগতিক দেখে নড়ে চড়ে বসলেন প্রাতিষ্ঠানিক কবি-সাহিত্যিকের দল । প্রতিটি বিষয়ের ওপর হাংরি আন্দোলনকরীদের আলাদা আলাদা ইস্তাহার ছিল । সাহিত্য বিষয়ক প্রথম ইস্তাহারটি লেখা হয় ইংরেজিতে, প্রকাশিত হয় ১৯৬১ সালে । কারণ সেটির রচয়িতা মলয় রায়চৌধুরী পাটনার বাসিন্দা, সেখানে কোনো বাংলা প্রেস নেই । পরে ১৯৬২ সালের এপ্রিলে বাংলায় ইস্তাহার প্রকাশিত হয় । ক্রিয়েটর মালয় রায়চৌধুরী, লিডার উল্টোডাঙা বস্তিতে সেই সময়ে বাস করা কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়, প্রকাশক ও সম্পাদক হাওড়ার এক বস্তিবাসী হারাধন ধাড়া ( দেবী রায় ) । কী ছিল সেই ইস্তাহারে ?
সেই ইস্তাহার ছিল এই রকম : মানুষ, ঈশ্বর, গণতন্ত্র পরাজিত । কবিতাই এখন একামাত্র আশ্রয় । এখন প্রয়োজন মেরুবিপর্যয়, প্রয়োজন অনর্থ বের করা । চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা থেকে জন্ম নেবে কবিতা । শিল্পের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কবিতা সৃষ্টির প্রথম শর্ত । ছন্দে গদ্য লেখার খেলাকে কবিতা নাম দিয়ে চালাবার চালাকি এবার শেষ হওয়া প্রয়োজন । টেবল ল্যাম্প ও সিগারেট জ্বালিয়ে, সেরিব্রাল কর্টেক্সে কলম ডুবিয়ে, কবিতা বানানোর কাল শেষ হয়ে গেছে । এখন কবিতা রচিত হয় অরগ্যাজমের স্বতঃস্ফূর্তিতে । অন্তরজগতের নিষ্কুন্ঠ বিদ্রোহ, অন্তরাত্মার নিদারুণ বিরক্তি, রক্তের প্রতিটি বিন্দুতে রচিত হবে কবিতা । অর্থব্যঞ্জনাঘন হোক বা ধ্বনি পারম্পর্যে শ্রুতিমধুর, বিক্ষুব্ধ প্রবল চঞ্চল অন্তরাত্মার ও বহিরাত্মার ক্ষুধা নিবৃত্তির শক্তি না থাকলে কবিতা সতীর মতো চরিত্রহীনা, প্রিয়তমার মতো যোনিহীনা ও ঈশ্বরীর মতন অনুন্মেষিনী হয়ে যেতে পারে ।
সাহিত্যে ছড়িয়ে পড়ল হাংরি আন্দোলন । একে একে এসে যোগ দিলেন বিনয় মজুমদার, উৎপলকুমার বসু, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, সুভাষ ঘোষ, প্রদীপ চৌধুরী, সুবো আচার্য, সুবিমল বসাক, শৈলেশ্বর ঘোষ, ত্রিদিব মিত্র, আলো মিত্র, অনিল করঞ্জাই, করুণানিধান মুখোপাধ্যায়, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, সমীর রায়চৌধুরী, বাসিদেব দাশগুপ্ত, অবনী ধর, রবিউল, শম্ভু রক্ষিত, তপন দাশ, এবং আরও অনেকে । তখনকার প্রচলিত রীতি মানেননি হাংরিরা, তাঁদের কোনো সম্পাদকীয় দপতর বা হেড কোয়ার্টার ছিল না। যে যার মতো করে ফালি কাগজে বুলেটিন বার করত, খরচ দিতেন মলয় এবং সমীর । পত্রিকাগুলোর নামও ছিল একেবারে ভিন্ন, স্বকাল, ফুঃ, চিহ্ণ, জেব্রা, জিরাফ, প্রতিদ্বন্দ্বী, উন্মার্গ, ওয়েস্ট পেপার, ধৃতরাষ্ট্র, কনসেনট্রেশন ক্যাম্প ইত্যাদি । প্রকাশিত বুলেটিনগুলি কফি হাউসে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, সংবাদপত্র দপতরে, কলেজে হাতে হাতে বিলি করা হতো ।
হাংরি আন্দোলন বহিরাগত এমন তকমা দিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক লেখকরা দল বাঁধতে লাগলেন ভিতরে ভিতরে । শক্তি চট্টোপধ্যায় তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেনকে উদ্দেশ্য করে ‘সীমান্ত পপস্তাব’ কবিতায় লিখলেন :
“কবিতা ভাতের মতো কেন লোকে নিতেই পারছেনা
যুদ্ধ বন্ধ হলে নেবে ? ভিখারিও কবিতা বুঝেছে
তুমি কেন বুঝবে না হে অধ্যাপক মুখ্যমন্ত্রী সেন?”
আগুনের মতো সব লেখা বেরিয়ে আসছে । নতুন ভাষা, নতুন আঙ্গিক, ঝরঝরে গদ্য, তথাকথিত অশ্লীল ও যৌনশব্দের মিশেল, একবার পড়লে আর একটা পড়তে ইচ্ছা হবে । গ্রন্হ প্রকাশিত হতে লাগল আন্দোলনকারীদের । শৈলেশ্বর ঘোষের ‘জন্মনিয়ন্ত্রণ’, সুভাষ ঘোষের ‘আমার চাবি’, ‘যুদ্ধে আমার তৃতীয় ফ্রন্ট’, ফালগুনী রায় লিখলেন ‘নষ্ট আত্মার টেলিভিশন’, বাসুদেব দাশগুপ্ত লিখলেন, ‘রন্ধনশালা’, সুবিমল বসাক লিখলেন ‘ছাতামাথা’, মলয় রায়চৌধুরী লিখলেন ‘শয়তানের মুখ’, ত্রিদিব মিত্র লিখলেন ‘হত্যাকাণ্ড’, প্রদীপ চৌধুরী লিখলেন ‘চৌষট্টি ভুতের খেয়া’, আরও অনেকের লেখা বই ।
আঁকার জগতে প্রসারিত হল হাংরি ভাবধারা । যোগ দিলেন অনিল করঞ্জাই, করুণানিধান মুখোপাধ্যায় । মাত্র সাতাশ বছর বয়সে অনিল করঞ্জাই দিল্লির ললিতকলা অ্যাকাডেমির পুরস্কার পেয়েছিলেন।
কলকাতায় আন্দোলনের ধারা ঝড় তুলেছে । বিভিন্ন জীবজন্তু, জোকার, রাক্ষস, দেবতার মুখোশ প্রতিষ্ঠানের কর্তাব্যক্তি, কবি, লেখক, সাংবাদিক, সরকারি আধিকারিকদের পাঠিয়ে বল হলো ‘দয়া করে মুখোশ খুলে ফেলুন’ । পত্রিকার দপতরে বাচ্চাদের চটির বাক্স পাঠিয়ে বলা হলো রিভিউ করতে । নিমতলা শ্মশানঘাট, মাইকেলের কবর, খালাসিটোলা-মদের আড্ডায় কবিতা উৎসব করলেন তাঁরা, হাওড়া স্টেশনে বেঞ্চে দাঁড়িয়ে কবিতা পড়লেন ত্রিদিব মিত্র ও মলয় রায়চৌধুরী । মাইকেল এবং জীবনানন্দ ছাড়া অন্য কোনও কাব্যপ্রতিভাকে স্বীকার করতেন না তাঁরা । রবীন্দ্রনাথকে তাঁর গানের জন্য শ্রদ্ধা করতেন । রবীন্দ্রনাথের গান গাইতেন বাসুদেব দাশগুপ্ত ও মলয় রায়চৌধুরী ।
হাংরি আন্দোলনের সংবাদ বিদেশেও পৌঁছালো । আমেরিকার ‘টাইম’ ম্যাগাজিনে ফোটোসহ হাংরি আন্দোলনকারীদের সংবাদ প্রকাশিত হবার পর ভারতের অন্যান্য ভাষায় ছড়িয়ে পড়ল । ১৯৬৩ সালে মলয় রায়চৌধুরীর সঙ্গে পাটনায় গিয়ে দেখা করলেন বিট আন্দোলনের কবি অ্যালেন গিন্সবার্গ । বেনারসে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হল অনিল করঞ্জাই ও করুণানিধান মুখোপাধ্যায়ের। কলকাতার প্রাতিষ্ঠানিক লেখকরা প্রশাসনের ওপর চাপ সৃষ্টি করলেন হাংরি আন্দোলনকারীদের ওপর পুলিশি অ্যাকশান নেবার জন্য । ১৯৬৪ সালে পুলিশ তাঁদের ওপর অ্যাকশান নেয়া আরম্ভ করলে, আমেরিকা থেকে অ্যালেন গিন্সবার্গ হাংরি আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে কমিটি ফর কালচারাল ফ্রিডাম এর কর্তাব্যক্তি আবু সয়ীদ আইয়ুবকে ১৯৬৪ সালের ৬ই অক্টোবর চিঠি লেখেন :-
“আপনার বাগাড়ম্বর আমাকে বিভ্রান্ত করে তুলছে । মাথা গরম করে দিচ্ছে আমার । আপনি প্রতিষ্ঠিত লেখক নন ? ‘আমার কোনো পদমর্যাদা নেই’, এসব কথার মানে কি ? ইনডিয়ান কমিটি ফর কালচারাল ফ্রিডাম-এর উদ্যোগে চলা চতুর্মাসিক পত্রিকার সম্পাদক আপনি । আপনার নিজস্ব লেটারহেড আছে । ভারতীয় কমিটির এগজিকিউটিভদের তালিকা আপনার হাতের কাছেই আছে । বাগাড়ম্বর বলতে আমি বোঝাতে চাইছি আপত্তিকর উপাদানের কথা । মশায়, আপনি এবং পুলিশই একমাত্র লেখাগুলি আপত্তিকর বলছেন । আমি আপনাদের আপত্তি তোলা নিয়েই প্রশ্ন করছি । পুলিশ নিজেদের ও অন্যদের রক্ষণশীল সাহিত্যরুচি চাপিয়ে দিচ্ছে জোর করে । ” ( দেশ, অক্টোবর, ২০১৫ )
আবু সয়ীদ আইয়ুব অ্যালেন গিন্সবার্গকে জবাবে বলেন, “আই ডু নট অ্যাগ্রি উইথ ইউ দ্যাট ইট ইজ দি পপাইম টাস্ক অব দি কমিটি ফর কালচারাল ফ্রিডাম টু টেক আপ দিস কজ অব দিস ইমম্যাচিয়র ইমিটেটরস অব আমেরিকান পোয়েট্রি।”
আবু সয়ীদ আইয়ুবের উষ্মার কারণ ছিল । মলয় রায়চৌধুরী সেসময়ে প্রাতিষ্ঠানিক কবি-লেখকদের উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, “ফাক দি বাস্টার্ডস অব গাঙশালিক স্কুল অব পোয়েট্রি”। কথাগুলি একটি বিয়ের কার্ডে ছাপিয়ে সাহিত্যিকদের পাঠানো হয়েছিল ।মলয়ের দেওয়া অভিধা আইয়ুব সাহেবকে আঘাত করে থাকবে ।
বিরোধের কারণ হল, ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত একটি হাংরি বুলেটিনে মলয় রায়চৌধুরীর লেখা ‘প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার’ ( Stark Electric Jesus ) কবিতাটি, যার বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগ ওঠে । এছাড়াও ওই কবিতায় প্রচলিত কাব্যভাষার বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ ছিল । কবিতাটি এখানে দেয়া হল:
ওঃ মরে যাব মরে যাব মরে যাব
আমার চামড়ার লহমা জ্বলে যাচ্ছে অকাট্য তুরুপে
আমি কী কোর্বো কোথায় যাব ওঃ কিছুই ভাল্লাগছে না
সাহিত্য-ফাহিত্য লাথি মেরে চলে যাব শুভা
শুভা আমাকে তোমার তর্মুজ আঙরাখার ভেতর চলে যেতে দাও
চুর্মার অন্ধকারে জাফ্রান মশারির আলুলায়িত ছায়ায়
সমস্ত নোঙর তুলে নেবার পর শেষ নোঙর আমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে
আর আমি পার্ছি না, অজস্র কাঁচ ভেঙে যাচ্ছে কর্টেক্সে
আমি জানি শুভা, যোনি মেলে ধরো, শান্তি দাও
প্রতিটি শিরা অশ্রুস্রোত বয়ে নিয়ে যাচ্ছে হৃদয়াভিগর্ভে
শাশ্বত অসুস্হতায় পচে যাচ্ছে মগজের সংক্রামক স্ফুলিঙ্গ
মা, তুমি আমায় কঙ্কালরূপে ভূমিষ্ঠ করলে না কেন ?
তাহলে আমি দুকোটি আলোকবষহ ঈশ্বরের পোঁদে চুমো খেতুম
কিন্তু কিছুই ভলো লাগছে না আমার কিচ্ছু ভালো লাগছে না
একাধিক চুমো খেলে আমার গা গুলোয়
ধর্ষণকালে নারীকে ভুলে গিয়ে শিল্পে ফিরে এসেছি কতদিন
কবিতার আদিত্যবর্ণা মূত্রাশয়ে
এসব কী হচ্ছে জানি না তবু বুকের মধ্যে ঘটে যাচ্ছে অহরহ
সব ভেঙে চুরমার করে দেব শালা
ছিন্নভিন্ন করে দেব তোমাদের পাঁজরাবদ্ধ উৎসব
শুভাকে হিঁচড়ে উঠিয়ে নিয়ে যাব আমার ক্ষুধায়
দিতেই হবে শুভাকে
ওঃ মলয়
কোল্কাতাকে আর্দ্র ও পিচ্ছিল বরাঙ্গের মিছিল মনে হচ্ছে আজ
কিন্তু আমাকে নিয়ে আমি কী কোর্বো বুঝতে পার্ছি না
আমার স্মৃতিশক্তি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে
আমাকে মৃত্যুর দিকে যেতে দাও একা
আমাকে ধর্ষণ ও মরে যাওয়া শিখে নিতে হয়নি
প্রস্রাবের পর শেষ ফোঁটা ঝাড়ার দায়িত্ব আমায় শিখতে হয়নি
অন্ধকারে শুভার পাশে গিয়ে শুয়ে পড়া শিখতে হয়নি
শিখতে হয়নি নন্দিতার বুকের ওপর শুয়ে ফরাসি চামড়ার ব্যবহার
অথচ আমি চেয়েছিলুম আলেয়ার নতুন জবার মতো যোনির সুস্হতা
যোনোকেশরে কাঁচের টুকরোর মতন ঘামের সুস্হতা
আজ আমি মগজের শরণাপন্ন বিপর্যয়ের দিকে চলে এলুম
আমি বুঝতে পার্ছি না কী জন্যে আমি বেঁচে থাকতে চাইছি
আমার পূর্বপুরুষ লম্পট সাবর্ণচৌধুরীদের কথা আমি ভাবছি
আমাকে নতুন ও ভিন্নতর কিছু কোর্তে হবে
শুভার স্তনের ত্বকের মতো বিছানায় শেষবার ঘুমোতে দাও আমায়
জন্মমুহূর্তের তীব্রচ্ছটা সূর্যজখম মনে পড়ছে
আমি আমার নিজের মৃত্যু দেখে যেতে চাই
মলয় রায়চৌধুরীর প্রয়োজন পৃথিবীর ছিল না
তোমার তীব্র রূপালি য়ূটেরাসে ঘুমোতে দাও কিছুকাল শুভা
শান্তি দাও, শুভা শান্তি দাও
তোমার ঋতুস্রাবে ধুয়ে যেতে দাও আমার পাপতাড়িত কঙ্কাল
আমাকে তোমার গর্ভে আমারই শুক্র থেকে জন্ম নিতে দাও
আমার বাবা-মা আন্য হলেও কি আমি এরকম হতুম ?
সম্পূর্ণ ভিন্ন এক শুক্র থেকে মলয় ওর্ফে আমি হতে পার্তুম ?
আমার বাবার অন্য নারীর গর্ভে ঢুকেও কি মলয় হতুম ?
শুভা না থাকলে আমিও কি পেশাদার ভদ্রলোক হতুম মৃত ভায়ের মতন ?
ওঃ বলুক কেউ এসবের জবাবদিহি করুক
শুভা, ওঃ শুভা
তোমার সেলোফেন সতীচ্ছদের মধ্যে দিয়ে পৃথিবীটা দেখতে দাও আমায়
পুনরায় সবুজ তোশকের ওপর চলে এসো শুভা
যেমন ক্যাথোড রশ্মিকে তীক্ষ্ণধী চুম্বকের আঁচ মেরে তুলতে হয়
১৯৫৬ সালের সেই হেস্তনেস্তকারী চিঠি মনে পড়ছে
তখন ভাল্লুকের ছাল দিয়ে সাজানো হচ্ছিল তোমার ক্লিটোরিসের আশপাশ
পাঁজর নিকুচি করা ঝুরি তখন তোমার স্তনে নামছে
হুঁশাহুঁশহীন গাফিলতির বর্ত্মে স্ফীত হয়ে উঠছে নির্বোধ আত্মীয়তা
আ আ আ আ আ আ আ আ আ আঃ
মরে যাব কিনা বুঝতে পার্ছি না
তুল্কালাম হয়ে যাচ্ছে বুকের ভেতরকার সমগ্র অসহায়তায়
সব কিছু ভেঙে তছনছ করে দিয়ে যাব
শিল্পের জন্যে সক্কোলকে ভেঙে খান-খান করে দোব
কবিতার জন্যে আত্মহত্যা ছাড়া স্বাভাবিকতা নেই
শুভা
আমাকে তোমার লাবিয়া ম্যাজোরার স্মরণাতীত অসংযমে প্রবেশ কোর্তে দাও
দুঃখহীন আয়াসের অসম্ভাব্যতায় যেতে দাও
বেসামাল হৃদয়বত্তার স্বর্ণসবুজে
কেন আমি হারিয়ে যাইনি আমার মায়ের যোনিবর্ত্মে ?
কেন আমি পিতার আত্মমৈথুনের পর তাঁর পেচ্ছাপে বয়ে যাইনি ?
কেন আমি রজোস্রাবে মিশে যাইনি শ্লেষ্মায় ?
অথচ আমার নীচে চিত আধবোজা অবস্হায়
আরামগ্রহণকারিণী শুভাকে দেখে ভীষণ কষ্ট হয়েছে আমার
এরকম অসহায় চেহারা ফুটিয়েও নারী বিশ্বাসঘাতিনী হয়
আজ মনে হয় নারী ও শিল্পের মতো বিশ্বাসঘাতিনী কিছু নেই
এখন আমার হি২স্র হৃৎপিণ্ড অসম্ভব মৃত্যুর দিকে যাচ্ছে
মাটি ফুঁড়ে জলের ঘূর্ণি আমার গলা ওব্দি উঠে আসছে
আমি মরে যাব
ওঃ এসমস্ত কী ঘটছে আমার মধ্যে
আমি আমার হাত হাতের চেটো খুঁজে পাচ্ছি না
পায়জামায় শুকিয়ে-যাওয়া বীর্য থেকে ডানা মেলছে
৩০০০০০ শিশু উড়ে যাচ্ছে শুভার স্তনমণ্ডলীর দিকে
ঝাঁকে-ঝাঁকে ছুঁচ ছুটে যাচ্ছে রক্ত থেকে কবিতায়
এখন আমার জেদি ঠ্যাঙের চোরাচালান সেঁদোতে চাইছে
হিপ্নোটিক শব্দরাজ্য থেকে ফাঁসানো মৃত্যুভেদী যৌনপর্চুলায়
ঘরের প্রত্যেকটা দেয়ালে মার্মুখি আয়না লাগিয়ে আমি দেখছি
কয়েকটা ন্যাংটো মলয়কে ছেড়ে দিয়ে তার আপ্রতিষ্ঠিত খেয়োখেয়ি
তৎকালীন কবি-সাহিত্যিকরা হাংরি আন্দোলনকারীদের ক্ষুধার্ত ভাষা সম্পর্কে আতঙ্কিত হচ্ছিলেন । প্রচারের সব আলো তখন হাংরি আন্দোলনের দিকে । সরকার বিব্রত হচ্ছিল হাংরি আন্দোলনকারীদের বৌদ্ধিক আক্রমণে । একটি লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদক ( পবিত্র বল্লভ ), কয়েকজন কবি এবং পুলিশের ইনফরমাররা গোপনে তথ্য, বুলেটিন, পত্রিকা, হাংরিদের ঠিকানা ইত্যাদি যোগাড় করতে লাগল, তাদের বিরুদ্ধে পুলিশি অ্যাকশান নেবার জন্য । পরিশেষে ছাব্বিশজন কবিকে লালবাজারে ডেকে জেরা করা হল । ওয়ারেন্ট ইশ্যু করা হল এগারোজনের বিরুদ্ধে । বুলেটিনের প্রকাশক হিসাবে সমীর রায়চৌধুরী গ্রেপ্তার হলেন চাইবাসা থেকে । তিনি সেখানে ছিলেন ডিস্ট্রিক্ট ফিশারিজ অফিসার । কলকাতার পুলিশ পাটনায় গিয়ে মলয় রায়চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করল । গ্রেপ্তারের পর পুলিশ ইন্সপেক্টররা রিকশায় বসলেন এবং মলয়কে হাতে হাতকড়া ও কোমরে দড়ি বেঁধে চোরডাকাতের মতন রাস্তা দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হল । বাড়ি লণ্ডভণ্ড করে বহু লেখাপত্র নষ্ট করে দেওয়া হল। ফাইল, বইপত্র, টাইপরাইটার ইত্যাদি বগলদাবা করে কলকাতায় নিয়ে গেল লালবাজার পুলিশ, যা আর পরে ফিরে পাননি হাংরি আন্দোলনকারীরা। শৈলেশ্বর ঘোষ ও সুভাষ ঘোষ গ্রেপ্তার হল কলকাতায় । তাদের কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে আগরতলা থেকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে এলো প্রদীপ চৌধুরীকে । দেবী রায়কে বর্ধমানে পোস্টাফিসের দপতর থেকে গ্রেপ্তার করে আনা হল । সুবো আচার্য আগরতলা থেকে এক উপজাতি গ্রামে পালিয়ে গিয়েছিলেন, পুলিশ তাঁকে ধরতে পারেনি । সকলকে জিজ্ঞাসাবাদ করে, শৈলেশ্বর ঘোষ ও সুভাষ ঘোষকে দিয়ে মলয় ও হাংরি আন্দোলনের বিরুদ্ধে মুচলেকা লিখিয়ে ছেড়ে দেয়া হয় । মলয়ের বিরুদ্ধে মুচলেকা লিখে দিয়েছিলেন সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায় ও উৎপলকুমার বসু — এনারা মলয়ের বিরুদ্ধে সরকার পক্ষের সাক্ষী হয়েছিলেন । শৈলেশ্বর ঘোষ ও সুভাষ ঘোষ মলয়ের বিরুদ্ধে রাজসাক্ষী হতে রাজি হয়ে ছাড়া পান । ১৯৬৫ সালে নিম্ন আদালতে ( ব্যাংকশাল কোর্ট ) মলয়ের দণ্ডাদেশ হয় । মলয় এর বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল করেন ।
কলকাতায় যখন হাংরি আন্দোলন নিয়ে তোলপাড় চলছে , সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তখন মার্কিন সরকারের টাকায় গেছেন আমেরিকার আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে কবিতার কর্মশালায় যোগ দিতে । ‘কৃত্তিবাস’ পত্রিকা সামলাচ্ছেন শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় । স্বাভাবিকভাবেই সুনীল বেশ উদ্বিগ্ন । তাঁর অবর্তমানে কলকাতা দখল করে নিচ্ছে একদল তরুণ, এবং তিনি এই বিষয়ে কিছুই জানেন না ; বন্ধুদের চিঠি পেয়ে তাঁর উদ্বেগ বাড়ছে । ১৯৬৪ সালের ১০ই জুন একটি চিঠিতে সুনীল আইওয়া থেকে মলয়কে লিখলেন, “কলকাতা শহরটা আমার, ফির গিয়ে আমি ওখানে রাজত্ব করব । দু’একজন বন্ধুবান্দব ওই দলে আছে বলে নিতান্ত স্নেহবশতই তোমাদের হাংরি জেনারেশন গোড়ার দিকে ভেঙে দিইনি । এখনও সে ক্ষমতা রাখি । লেখার বদলে হাঙ্গামা ও আন্দোলন করার দিকেই তোমার লক্ষ্য বেশি । যতো খুশি আন্দোলন করো, বাংলা কবিতার এতে কিছু এসে যায় না ।” আসলে সুনীলও প্রাতিষ্ঠানিক লেখকদের মতো হাংরি আন্দোলনের জনপ্রিয়তা ও বিস্তার নিয়ে শঙ্কিত হচ্ছিলেন । আমেরিকার লিটল ম্যাগাজিনে হাংরি আন্দোনকারীদের রচনা তাঁর চোখের সামনেই প্রকাশিত হচ্ছিল । উক্ত চিঠিতে সেই উদ্বেগের প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে ।
কলকাতা হাইকোর্টে মলয়ের মামলাটি ওঠে বিচারক তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের এজলাসে ।মলয়ের হয়ে মামলাটি হাইকোর্টে লড়েছিলেন ব্যারস্টার মৃগেন সেন ও তাঁর চারজন সহকারী । মৃগেন সেনের কাছে মলয়কে নিয়ে গিয়েছিলেন সদ্য লণ্ডন থেকে ফেরা ব্যারিস্টার, জ্যোতির্ময় দত্তের বন্ধু, করুণাশঙ্কর রায় ।
ব্যাংকশাল কোর্টে মলয়ের বিরুদ্ধে প্রথম সাক্ষ্য দিয়েছিলেন ‘উপদ্রুত’ পত্রিকার সম্পাদক পবিত্র বল্লভ । এর পর লালবাজারের জাল সাক্ষী দিয়ে গেলেন এক অফিসার যিনি মলয় রায়চৌধুরীকে পাটনা থেকে গ্রেপ্তার করে এনেছিলেন । এরপর শক্তি চট্টোপাধ্যায়, যিনি প্রথম হাংরি ইস্তাহারে লিডার ছিলেন । এছাড়াও মলয়ের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়ে গেলেন সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, উৎপলকুমার বসু, অন্য দুই হাংরি শৈলেশ্বর ঘোষ ও সুভাষ ঘোষ । তারপর মলয়ের পক্ষের সাক্ষীরা । প্রথমে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, ভরা আদালতে দাঁড়িয়ে বিচারককে জানালেন কবিতাটি অবসিন নয়, ভালগারও নয়, কবিতাটিতে নামমাত্র অশ্লীলতা আছে বলে তিনি মনে করেন না । একে একে সাক্ষ্য দিলেন তরুণ সান্যাল, কবি বুদ্ধদেব বসুর জামাতা জ্যোতির্ময় দত্ত, কবি অজিত দত্ত’র মার্কিন-প্রবাসী পুত্র সত্রাজিৎ দত্ত । মলয়ের পক্ষে এতোজনের সাক্ষ্য সত্ত্বেও বিচারক অমলকুমার মিত্র মলয়ের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদানকারীদের বক্তব্যের ওপর নির্ভর করে দণ্ডাদেশ দিয়েছিলেন।
কলকাতা হাইকোর্ট মলয়কে ১৯৬৭ এর জাজমেন্টে বেকসুর খালাস করে দেন । মলয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগকে নাকচ করে দেন বিচারক । এই ঘটনাটি আন্তর্জাতিক পত্র-পত্রিকায় ভালো রকমের সাড়া ফেললো । টাইম ম্যাগাজিন লিখলো, ‘ক্যালকাটাজ হাংরি জেনারেশন ইজ এ গ্রোইং ব্যাণ্ড অব ইয়ং বেঙ্গলি টাইগার্স উইথ টাইগার্স ইন দেয়ার ট্যাঙ্কস’।
মলয়ের ‘প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার’কবিতাটির ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হল ওয়াশিংটন স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে, ‘স্টার্ক ইলেকট্রিক জেশাস’ নামে যা হাওয়ার্ড ম্যাককর্ড অনুবাদ করেছিলেন । কবিতাটি এবং তাঁর কোর্ট কেসের সংবাদ তার আগে প্রকাশিত হয়েছিল লরেন্স ফেরলিংঘেট্টি সম্পাদিত ‘সিটি লাইটস জার্নাল’ পত্রিকায় । এই সিটি লাইটস থেকেই প্রকাশিত হতো বিট আন্দোলনের কবি ও লেখকদের বই ।
১৯৬৪ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর ব্লিৎস পত্রিকায় এক পৃষ্ঠাব্যাপী হাংরি আন্দোলনের খবর প্রকাশিত হল । তাতে বলা হল, “পুলিশ ন্যাব ক্যালকাটা বিটনিকস । ইরটিক লাইভস অ্যাণ্ড লাভস অব হাংরি জেনারেশন।”
আন্দোলন তুঙ্গে থাকার সময়ে আনন্দবাজার, যুগান্তর, সাপ্তাহিক জনতা নামের সংবাদপত্রগুলিতে নিয়মিত হাংরি আন্দোলনের খবর গুরুত্ব সহকারে প্রকাশিত হতো । দৈনিক স্টেটসম্যান, যুগান্তর, আনন্দবাজর পত্রিকায় মলয় ও দেবী রায়ের কার্টুন প্রকাশিত হয়েছিল। সেই সময়ে জনতা পত্রিকার প্রথম পাতায় একবার মলয়ের আকটি কার্টুন প্রকাশিত হল । উপরে শিরোনাম “কল্লোল যুগের প্রৌঢ় কবিও কি হাংরি?” কার্টুনের তলায় বুদ্ধদেব বসুর সাম্প্রতিক একটি লেখা থেকে কয়েক লাইন । উদ্ধৃত অংশটি লেখার কিছুদিন আগেই বুদ্ধদেব বসু আমেরিকা গিয়েছিলেন । লেখাটিতে বুদ্ধদেব বসুর এরকম লাইন ছিল, “শিথিল শাড়ি, সোনালী শরীর গলে যায় ধীরে, স্তনের বোঁটা, চোখের মতো কাঁপছে । টার পাই তার স্তন দুটি উঁচু হয়ে আমাকে দেখছে । বলি, থামো, যেও না, ময়লা জিনের প্যান্টালুন থেকে বেরিয়ে আসবে তলোয়ার, জ্বলবে আমার আগুন তোমার জোয়ারে । জবাবে সে মাথার তলা থেকে বালিশ ফেলে দেয়, দমকা হাওয়ায় উড়িয়ে দেয় শাড়ি, তার উদর পালের মতো এগিয়ে আসে । এখনও তবু আমি লুব্ধ । হাড়ে হাড়ে অমর কাম ক্ষমাহীন।”
এই লেখাটি প্রমাণ করে যে কেবল যৌন শব্দপ্রয়োগের জন্যই মলয় রায়চৌধুরী আক্রান্ত হননি । তাহলে বুদ্ধদেব বসুও হতেন । আসল কারণ ছিল প্রতিষ্ঠানবিরোধিতা । প্রতিষ্ঠান চায়, ব্যক্তিএকক চিরকাল সরকার ও ক্ষমতাবান প্রাতিষ্ঠানিকদের পদানত থাকবে । এটাই সত্য । মলয়ের অসহ্য উপস্হিতি, সরকার ও প্রাতিষ্ঠানিক কর্তাদের বিব্রত করছিল । তাই সকলকে ছেড়ে দিলেও মলয় রায়চৌধুরীকে মামলার মুখোমুখি হতে হয় । হাতে হাতকড়া, কোমরে দড়ি বেঁধে তাঁকে রাস্তা দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় । হাংরি আন্দোলন মামলা চলাকালীন বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন মলয়, তাঁর কবিতা ভবনের বাড়িতে গিয়ে । বুদ্ধদেব বসু দেখা করতে চাননি ; মলয় পরিচয় দিতেই দরোজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন ।
এখন দেখা যাক মলয় রায়চৌধুরী মানুষটা কেমন । কিসের জোরে হাংরি আন্দোলনের মতো এতো বড়ো উথালপাথাল ঘটিয়ে দিতে পারলেন, তার জন্ম দিলেন, তাকে লালন করলেন, অংশগ্রহণকারীদের একত্রিত করে প্রকৃত নেতৃত্ব দিলেন । বাংলা কবিতার খোলনলচে পালটে দিয়ে জেল খাটলেন কবিতা লেখার জন্য । সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো প্রাতিষ্ঠানিক লেখককে ভয় পাইয়ে দিলেন । মলয় রায়চৌধুরী, যিনি একটি কবিতায় লিখেছিলেন, সাহিত্যের আধুনিকতাবাদ একটি ‘ধ্রুপদী জোচ্চোর’ ।
মলয় ১৯৩৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন পাটনা শহরের ইমলিতলা নামের এক অন্ত্যজ অধ্যুষিত পাড়ায়, যেখানে ডোম, মেথর, দুসাধ, চামার, কুমোর, দরিদ্রতম মুসলমান পরিবারের বসবাস ।
মলয়ের শৈশব কেটেছে প্রত্যহ সন্ধ্যায় শূকরের মৃত্যুকালীন আর্ত-চিৎকার শুনে । পাড়ার গরিব অন্ত্যজরা শুকরের মাংস খেতো । শূকরকে মারার জন্য প্রাণীটাকে একটা গর্তে ফেলে দিয়ে তার দেহে গনগনে লোহার শিক বিঁধে দিত, আর তার মৃত্যকালীন চিৎকারে ভারি হয়ে উঠত মহল্লার বাতাস । কম বয়সি বাচ্চাদের মুখে ফিরত “পুরি কচৌড়ি তেল মে, জিন্না বেটা জেল মে।”
মলয় প্রাথমিক শিক্ষা পান পাটনা শহরের মিশনারি স্কুলে । মিশনারি স্কুলের চার্চের ফাদার হিলম্যান মলয়ের বাবার ফোটোর দোকানের ক্রেতা ছিলেন ; তাঁরই সহযোগিতায় মলয় ভর্তি হন, এবং তাঁর ফিসও মুকুব করে দেয়া হয়েছিল । তারপর ক্লাস সিক্স থেকে ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়েন ব্রাহ্ম স্কুল রামমোহন রায় সেমিনারিতে । পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৮ সালে অর্থনীতিতে সান্মানিক স্নাতক হন, দ্বিতীয় স্হান অধিকার করেন । ১৯৬০ সালে অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর হন, এবং পুনরায় বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় স্হান অধিকার করেন । পাশ করা মাত্র তিনি ভাগলপুর ও শিলঙে অধ্যাপকের চাকরি পেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর বাবা-মা তাঁদের একা ছেড়ে যেতে বারন করেন । মলয়ের দাদা সমীর রায়চৌধুরী ডিস্ট্রিক্ট ফিশারিজ অফিসার হিসাবে বিহারের বিভিন্ন জেলা সদরে চাকরি করতেন । বাবা-মাকে দেখার আর কেউ ছিল না । মলয়রা দুই ভাই, কোনও বোন নেই ।
পাটনার অতিদরিদ্র ইমলিতলা পাড়ায় বসবাস করলেও, মলয়ের একটি উজ্জ্বল পারিবারিক অতীত আছে । বড়িশা-বেহালার সাবর্ণ চৌধুরী বংশের সপ্তম প্রজন্ম মলয় । বাবা রঞ্জিত রায়চৌধুরী, মা অমিতা রায়চৌধুরী । মলয়ের বাবা ও দাদুর কোনো বিদ্যায়তনিক শিক্ষা চিল না । দাদু ফারসি, আরবি, উর্দু লিখতে পড়তে পারতেন, কিন্তু ইংরেজি জানতেন না । সেই অর্থে মলয় এবং দাদা সমীরই স্কুল-কলেজে শিক্ষিত প্রথম প্রজন্ম । মলয়ের বাবার ঠাকুর্দা সাবর্ণ চৌধুরী পরিবার থেকে বিতাড়িত হন মুখোপাধ্যায় পরিবারের বাল্য বিধবাকে বিবাহের কারণে । মলয়ের বাবার পাটনায় ফোটোগ্রাফির দোকান ছিল, ব্যবসাটি পত্তন করেছিলেন মলয়ের ঠাকুর্দা, সেসময়ে তা ছিল ভ্রাম্যমান ফোটোর ব্যবসা । ঠাকুর্দা বর্তমান পাকিস্তানের বিভিন্ন শহরে গিয়ে অভিজাত পরিবারের সদস্যদের ফোটো তুলে তা থেকে পেইনটিঙ আঁকতেন । মলয়ের জেঠামশায় প্রমোদ ছিলেন পাটনা মিউজিয়ামের ‘কিপার অব পেইনটিংস অ্যান্ড স্কাল্পচার’।
সাবর্ণ চৌধুরী পরিবারের বিদ্যাধর রায়চৌধুরীর কাছ থেকেই ১৬৯৮ সালে মাত্র তেরোশো টাকায় জোব চার্নক সুতানুটি, গোবিন্দপুর, কলিকাতা নামের তিনটি গ্রামের ইজারা নিয়ে কলকাতা নগরীর পত্তন করেন । নবাবের নির্দেশে তাঁরা ইজারা দিতে বাধ্য হয়েছিলেন ।ইস্ট ইনডিয়া কোম্পানির পরিবর্তে সিরাজ-উদ-দৌলার পক্ষ নেবার কারণে সাবর্ণ চৌধুরীরা অন্যান্য অভিজাত পরিবারের তুলনায় ব্রিটিশদের দাক্ষিণ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন, এবং তাঁরা ক্রমশ ছত্রভঙ্গ হয়ে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েন ।
বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনা করার সময় থেকেই মলয় মার্কসবাদ ও ইতিহাসের দর্শন নিয়ে পড়াশুনা ও লেখালিখি করছিলেন । ‘ইতিহাসের দর্শন’ শিরোনামে তিনি ‘বিংশ শতাব্দী’ পত্রিকায় একটি ধারাবাহিক রচনা লিখেছিলেন । দাদার বন্ধু কবি দীপক মজুমদারের পরামর্শেই তিনি ইতিহাসের পরিবর্তে ইতিহাসের দর্শনে আগ্রহী হন । ইতিহাসের দর্শন সম্পর্কিত বইগুলি পড়ার সময়ে মলয় ইতিহাসকার অসওয়াল্ড স্পেংলারের ‘দি ডিক্লাইন অব দি ওয়েস্ট’ বইটির সঙ্গে পরিচিত হন । ‘হাংরি’ শব্দটি মলয় পেয়েছিলেন ইংরেজ কবি জিওফ্রে চসারের ‘ইন দি সাওয়ার হাংরি টাইম’ বাক্যটি থেকে । অসওয়াল্ড স্পেংলারের বই এবং জিওফ্রে চসারের কবিতার লাইন মলয়কে হাংরি আন্দোলনের তাত্বিক ভিত গড়তে সাহায্য করেছিল ।
স্পেংলার বলেছিলেন, একটি সংস্কৃতি কেবল একটি সরলরেখা বরাবর যায় না, তা লিনিয়র নয়, তা একযোগে বিভিন্ন দিকে প্রসারিত হয় । তা হল জৈবিক প্রক্রিয়া, এবং সেকারণে সমাজটির নানা অংশ কোন দিকে কার বাঁকবদল ঘটবে, তা আগাম বলা যায় না । যখন কেবল নিজের সৃজনক্ষমতার ওপর নির্ভর করে, তখন সংস্কৃতিটি নিজেকে সমৃদ্ধ ও বিকশিত করতে থাকে ; তার নিত্য নতুন স্ফূরণ ঘটতে থাকে। কিন্তু একটি সংস্কৃতির অবসান সেই সময় থেকে আরম্ভ হয়, যখন তার নিজের সৃজনক্ষমতা ফুরিয়ে গিয়ে তা বাইরে থেকে যা পায় তা-ই ‘আত্মসাৎ’ করতে থাকে, খেতে থাকে, তার ক্ষুধা তখন তৃপ্তিহীন।
মলয় রায়চৌধুরীর মনে হয়েছিল, দেশভাগের ফলে পশ্চিমবঙ্গ এই ভয়ঙ্কর অবসাদের মুখে পড়েছে । কলকাতা থেকে পাণিহাটি যাবার সময়ে ( তাঁর দাদা সমীর পাণিহাটিতে মামার বাড়িতে থেকে কলকাতার সিটি কলেজে যাতায়াত করতেন ) মলয় ও সমীর উদ্বাস্তুদের অসহায় জীবন প্রত্যক্ষ করতেন প্রতিদিন, কলকাতার পথে দেখতেন বুভুক্ষুদের প্রতিবাদ মিছিল । ক্ষোভ, ক্রোধ, প্রতিবাদ প্রকাশ করার জন্য তাঁদের দুজনের মনে হয়েছিল হাংরি আন্দোলন জরুরি । মলয় মনে করতেন, তাঁরা না করলেও অন্যেরা এই ধরণের আন্দোলন করত, প্রতিষ্ঠানকে নাস্তানাবুদ করত ।
মলয়ের প্রথম বই প্রবন্ধের, ‘মার্কসবাদের উত্তরাধিকার’, ১৯৬২ সালে প্রকাশিত হয়েছিল, যার প্রকাশক ছিলেন শক্তি চট্টোপাধ্যায় । হাংরি আন্দোলনের সময়ে একটি কপি দেবী রায়ের কাছে রেখে বাকি কপি পেটরল ঢেলে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল । মলয় পরে বলেছিলেন, ওই পুড়িয়ে দেয়াটা ছিল একটা পলিটিকাল ব্লাণ্ডার । শোনা যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের ওপর ক্ষেপে গিয়ে শক্তির উল্টোডাঙা বস্তিবাড়ির সামনে বইগুলো জড়ো করে জ্বালিয়েছিলেন মলয় । তাঁর দ্বিতীয় বইটি ছিল কবিতার ; বইয়ের নাম শয়তানের মুখ, ১৯৬৩ সালে কৃত্তিবাস প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত, প্রকাশক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় । বাংলা ভাষায় আর দ্বিতীয় কবি অথবা লেখক নেই যাঁর গ্রন্হ শক্তি এবং সুনীল দুজনেই প্রকাশ করেছিলেন ।
মলয়ের গ্রন্হাবলী ও সাহিত্যচর্চাকে দুটি পর্বে ভাগ করা যায় । যার প্রথম পর্ব ছিল হাংরি আন্দোলন থেকে আরম্ভ করে জেল থেকে ছাড়া পাওয়া পর্যন্ত । অর্থাৎ ১৯৬১ থেকে ১৯৬৭ সাল । এই সময়পর্বে তিনি ‘জেব্রা’ নামের একটি পত্রিকার দুটি সংখ্যা প্রকাশ করেন এবং শতাধিক হাংরি বুলেটিন প্রকাশের জন্য আর্থিক সাহায্য করেন । হাংরিদের পত্রিকার কভারের ব্লকও তিনি পাটনা থেকে করিয়ে এনে দিতেন । মলয়ের বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের বুদ্ধিজীবীরা পেরে উঠতেন না তার কারন মলয়ের গভীর পড়াশুনা ।
‘হাওয়া-৪৯’ পত্রিকায় মলয় সম্পর্কে উৎপলকুমার বসু লিখেছিলেন :-
“মলয় রায়চৌধুরী এখনকার বাংলা সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট নাম । তিনি ছয়ের দশকে লিখতে শুরু করেন এবং এখনও লিখছেন । তাঁর কবিতা, গদ্য, প্রবন্ধ, সাক্ষাৎকার, ইস্তাহার ও পোলেমিক্সের সমগ্র সংগ্রহ প্রকাশিত হলে একটি প্রয়োজনীয় কাজ হবে বলে আমার ধারণা। তিনি সাহিত্যিক নন । অর্থাৎ ‘সাহিত্যের সেবক’ বললে আমাদের স্মরণে যে ছবিটি ভেসে ওঠে, তাঁকে সেই শ্রেনিতে ফেলা যাবে না । বাংলা সাহিত্য তাঁর হাতে যতটা না পূজিত হয়েছে — আক্রান্ত হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি । গত চল্লিশ বছরে, বাংলা সাহিত্যের রণক্ষেত্রে যা-যা ঘটেছে, তা লিপিবদ্ধ করার যোগ্যতা বা ধৈর্য আমার নেই । তবে সংক্ষেপে এটুকু বলা যায় যে মলয় রায়চৌধুরী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়েই যুদ্ধে নেমেছিলেন । তাঁর তাত্বিক প্রস্তুতি ছিল । এবং তথাকথিত বাংলা ‘সংস্কৃতির’ ঘরে তাঁর লালন-পালন নয় বলে ওই কালচারের পীঠভূমিগুলিকে অবজ্ঞা করার মতো দুঃসাহস তিনি দেখিয়েছেন । বাংলা আধুনিক কবিতার প্রসঙ্গটি নিয়ে যদি ভাবা যায়, তবে দেখব, জীবনানন্দই সেই অঞ্চলের প্রধান পুরুষ । তাঁকে পিছনে ফেলে এগিয়ে না গেলে পরবর্তী একটা নতুন যুগের পত্তন হওয়া সম্ভব ছিল না । জীবনানন্দ কয়েকটি উপাদানকে অবলম্বন করেছিলেন । যেমন অভিনব ইমেজ, বা চিত্রকল্পের ব্যবহার, মআজাগতিক সচেতনতা,মানুষের উদ্যম ও প্রচেষ্টার প্রতি তীব্র অবজ্ঞা এবং সংশ্লিষ্ট আরও কয়েকটি গৌণ বিষয় । মলয় রায়চৌধুরী ও তাঁর প্রজন্মের লেখকদের ওই পাঠশালাতেই হাতে খড়ি হয়েছিল। কিন্তু অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তাঁদের অন্য ধরণের পথসন্ধান শুরু হয় । বাংলা সাহিত্যের প্রধান ধারাটি একপ্রকার স্হিতাবস্হায় পৌঁছে গিয়েছিল । তার বাঁধ ভেঙে দেওয়া ছাড়া অন্য উপায় ছিল না । তিনটি উপন্যাস ও স্মৃতিচারণেও মলয় রায়চৌধুরীর ওই আক্রমণকারী প্রবণতা লক্ষ করি । কথা প্রসঙ্গে তিনি একবার বলেছিলেন, ‘লেখা রাজনীতি ছাড়া আর কী হতে পারে?’ বলা বাহুল্য তিনি দলীয় বা সংসদীয় রাজনীতির কথা বলেননি । তিনি বলেছিলেন ‘পলিটির’ কথা । আমরা সবাই মিলে কীভাবে থাকব — মলয় রায়চৌধুরী তারই একটা বোঝাপড়ার দলিল তৈরি করেছেন।”
প্রথম পর্বের পর প্রচণ্ড অভিমান, ঘৃণা ও বিরক্তিতে মলয় তাঁর সমস্ত বইপত্র বিলিয়ে দিয়ে প্রথমে লখনউ ও পরে মুম্বাই চলে যান । রিজার্ভ ব্যাঙ্কে নোট পোড়াবার চাকরি ছেড়ে তিনি অ্যাগরিকালচারাল রিফাইনান্স ও ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনে যোগ দেন, এবং তখন থেকেই তিনি চাকুরিসূত্রে ভারতের গ্রামেগঞ্জে চাষি, তাঁতি, জেলে, কুমোর, চামার, ঝুড়ি প্রস্তুতকারী, খেতমজুর, ছুতোর প্রমুখ সমাজের তলার দিকের মানুষের জীবনযাত্রার সঙ্গে পরিচিত হন যা প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর উপন্যাস, গল্প ও প্রবন্ধে । এআরডিসি থেকে তিনি চলে যান নাবার্ডের মুম্বাই হেড অফিসে এবং ১৯৯৭ সালে অবসর নেন কলকাতা দপতরের ডেপুটি জেনারাল ম্যানেজার হিসাবে, পশ্চিমবঙ্গে সম্পর্কে প্রভূত অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পর ।
দ্বিতীয় পর্বের আত্মপ্রকাশ আটের দশকের মাঝামাঝি থেকে । মহদিগন্ত পত্রিকার সম্পাদক উত্তম দাশ তাঁর লখনউয়ের বাড়ি গিয়ে তাঁকে কবিতা সংকলন ও ইস্তাহারগুলির সংকলন প্রকাশে উৎসাহিত করেন । দুই পর্ব মিলিয়ে, এই রচনা লেখার সময় পর্যন্ত মলয়ের কাব্যগ্রন্হ চৌদ্দটি, উপন্যাস চৌদ্দটি, ছোটোগল্প সংকলন দুটি, নাটকের বই একটি, অগ্রন্হিত কাব্যনাটক তিনটি, প্রবন্ধ সংকলন সতেরোটি, স্মৃতিকথা দুটি, অনুবাদগ্রন্হ সাতটি, সাক্ষাৎকারগ্রন্হ চারটি — সব মিলিয়ে সত্তরটির মতো ।
সাতাত্তর বছর বয়সে এসে কমপিউটারে এক আঙুলে টাইপ করে লেখেন । এখনও সচল মস্তিষ্ক । চিকিৎসা বিভ্রাটে আর্থ্রাইটিসে সারা শরীরে ব্যথা নিয়ে কাজ করে চলেছেন । তরুন কবি ও লেখকদের বইয়ের ভূমিকা লিখে দিচ্ছেন । যৌবনের শুকনো নেশা, ক্যানাবিস, হ্যাশিস, মেস্কালিন, এলএসডি, আফিম, খালাসিটোলার বাংলা, পাটনার ঠররা, নেপালের ঠমেলে মোষের কাঁচা মাংস হরিণের মাংসের আচার আর গমের মদ ইত্যাদি থাবা বসিয়েছে স্বাস্হ্যের ওপর ।
মলয়ের যাবতীয় লেখালিখি সবই লিটল ম্যাগাজিনে । এপার বাংলা, বাংলাদেশে এবং যেখানে বাংলা ভাষার কাগজ প্রকাশিত হয় তার প্রায় সব কাগজেই মলয় কোনো না কোনো সময় লিখেছেন । প্রাতিষ্ঠানিক কোনো কাগজে মলয় কখনও একলাইনও লেখেননি । মলয় সম্ভবত একমাত্র লেখক যিনি তাঁর বইতে ঘোষণা করতেন যে তাঁর বইয়ের কারোর কোনো কপিরাইট নেই । প্রতিষ্ঠানবিরোধিতায় স্হির অবিচল মলয় ২০০৩ সালে ফিরিয়ে দিয়েছেন অকাদেমি সাহিত্য সন্মান । যদিও তাঁর এক সময়ের হাংরি বন্ধ শক্তি, সন্দীপন, উৎপল, সুবিমল মাথা পেতে সরকারিপুরস্কার নিয়েছেন । মলয়ের লেখালিখির ওপর পিএইচডি করেছেন আসাম বিশ্ববিদ্যলয়ের কুমার বিষ্ণু দে এবং রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদয়শঙ্কর বর্মা । এম ফিল করেছেন অনেকে, এখনও কয়েকজন করছেন । তাঁর উপন্যাসে জাদুবাস্তবতা নিয়ে গবেষণা করছেন অধ্যাপক শুভশ্রী দাশ ।গবেষণা করেছেন মার্কিন ছাত্রী মারিনা রেজা ।
‘মধ্যরাত্রি’ পত্রিকার সম্পাদক সৈয়দ সমিদুল ইসলাম একটি সাক্ষাৎকার মলয় রায়চৌধুরীকে প্রশ্ন করেছিলেন, “মলয়বাবু, আপনি কখনও নিশ্চয়ই ভেবে দেখেছেন, আপনি কী ? আপনি কে?”
জবাবে মলয় জানিয়েছিলেন, “আজিজুল হক তাঁর এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন, মলয় রায়চৌধুরী মানব সমাজের পেরিফেরির জীব, সোজা বাংলায় আমি একজন কালচারাল বা্টার্ড।”
( ‘নতুনপথ এই সময়’ পত্রিকার ১৪২৪ শরৎ সংখ্যায় প্রকাশিত )
 অর্ক চট্টোপাধ্যায় | 27.58.255.50 | ১০ আগস্ট ২০২১ ১৯:৫১734857
অর্ক চট্টোপাধ্যায় | 27.58.255.50 | ১০ আগস্ট ২০২১ ১৯:৫১734857অর্ক চট্টোপাধ্যায় : মলয় রায়চৌধুরীর গদ্য
ছোটোলোকের ছোটোবেলা
এবার আসি ১৯৯৯ – ২০০৩-এ লিখিত ও ২০০৪ সালে কোবার্ক পাবলিশাসফ প্রকাশিত আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস ‘ছোতোলোকের ছোটোবেলা’য় । “উপন্যাস” শব্দটি মলয়ের গদ্যের ক্ষেত্রে কতটা প্রযোজ্য তা অবশ্য বিতর্কসাপেক্ষ । উপনঅস হিল্পের ধারাটি তাঁর কাছে ঔপনিবেশিক আধুনিকতার ফসলমাত্র । এই ধারাটির ভাঙনলীলাই তাঁর চারণ এবং নড়ন-চড়ন । ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার সাথে মুখোমুখি হবার আগে ও পরে ভারতীয় সাহিত্যে এক দ্বিধাবিভক্তি লক্ষ্য করা যায় যে কারণে সমালোচিকা মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় “Twice born Indian Fiction” শব্দবন্ধটি ব্যবহার করেছেন । ভারতীয় সাইত্যের এই দোআঁশলা রূপ মলয়ের গদ্যের আনাচে-কানাচে । গল্প বলার থেকে বেশি না-বলা, না বলতে পারা । প্রতিটা গল্পই শুরু হয় হবে হবে করে তারপর আর হয় না, ফুরিয়ে যায় , ফুরোয় না শুধু অনন্ত সিরিজ— গল্প থেকে গল্পান্তর । বদলে যায় । বদলে বদলে যায় । এমনই এক বহুরৈখিক ন্যারেটিভ ট্যানজেন্টের গদ্য হল মলয় রায়চৌধুরীর “উপন্যাস” ।
প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতা ইওরোপীয় আভান্ত গার্দের মতই এক প্রতিশিল্প ( anti-art ) ও প্রতিসন্দর্ভবাদী অবস্হান বা অনবস্হান তৈরি করে —মলয়ের অভিযোগ— “শিল্প-সংস্কৃতি, প্রতিভা, মাস্টারপিস, এইরকম যাবতীয় কনসেপ্ট এনেছিল সাম্রাজ্যবাদীরা” । ‘হাওয়া-৪৯’কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন ইংরেজরা আসার পর রবীন্দ্রনাথ ও সুনীতিবাবু মিলে ‘আর্ট’ থেকে ‘কলা’র অনুবাদ-কাঠামো খাযা করেছেন গূঢ় নান্দনিক অভিসন্ধি নিয়ে । মলয় তাই স্বঘোষিতভাবেই প্রতি-লেখক । মলব যখন বলেন—“আসলে ইতিহাসকে বা কালকে বাদ দিয়ে এবার ভূগোল বা স্আনকে গুরুত্ব দিতে হবে”, তখন তাঁর কথায় উত্তরআধুনিকতায়, আধুনিকতার সময়ের মতো, স্হানিকতার গুরুত্বের জায়গাটা পরিষ্কার হয়ে যায় । স্হানিক এবং খণ্ডীকৃত প্রতর্কই মহাসন্দর্ভের বিরোধিতা করে এক বিকল্প ইতিহাস নির্মাণে সচেষ্ট হয় । “ছোটোলোকের ছোটোবেলা” তেমনই এক “local history”—মলয়ের সাংস্কৃতিক সংকরায়ণের কাইনি, যেখানে প্রাব মহাকাব্যের ঢঙে অসংখ্য ও বিচিত্র প্লট ও ক্যারেক্টার দেখা দেয় । একটি প্যারাগ্রাফ শেষ হতে না হতেই হারিয়ে যায় । অধুনান্তিক কাহিনি দর্শনে অসমাপ্ত ও অসমাপ্য এই গল্পগুলিই হল এক-একটি ট্যানজেন্ট । ট্রিলজির “লেখকের কথা” শীর্ষক অংশে তিনি লেখেন তাঁর গল্পের গড়াপেটা হল —“প্রট্যাগনিস্ট-কেন্দ্রিক মেট্রপলিটান সাহিত্য বহির্ভূত এমনই এক প্রারম্ভ যার বুনোট কিছুটা এগোলে চরিত্রেরা ফুরিয়ে এবং হারিয়ে যেতে থাকে । যেমনটা ভারতীয় সমাজে ঘটতে থাকে।” এই সতত বিলীয়মানতা মলয়ের মুসাফির অপরীকৃত জীবন ও তাঁর চারপাশে সাবর্ণ চৌধুরীদের একান্নবর্তি পরিবারে ভাঙনেরও চালচিত্র হয়ে যায় । যেমন নিজের মেজমামা ছ্যানের মৃত্যুতে লেখা ছোটোগল্পে মলয় পুরো গল্পটা লেখেন ন্যারেটিভকে হাইপোথিসিসে বদলে দিয়ে । ছ্যানের জীবনের প্রতিটি গল্পেরই এক বিকল্প বা প্রতি-গল্প ( anti-narrative ) আছে । সত্য তাই অনির্ণেয়ই থেকে যায় । প্যারাগ্রাফগুলি এক-একটি গল্প ও তার বিকল্পকে নির্ভার টেক্সট বানিয়ে পরপর সাজিয়ে ফেলে ।
ইতিহাসের এমনই লীনতাপ পাটনাত বাখরগঞ্জ এলাকার ইমলিতলার ছোটোলোক পাড়ায় । সেকানে চেয়ারে বসা বা রোজ স্নান করা বিলাসিতামাত্র । ন্যারেটিভ পেন্ডুলামের মতো পায়চারি করে ১৭০৯ সনে রত্নেশ্বর রায়চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত উত্তরপাড়ায় । উত্তরপাড়ার সাবর্ণ ভিলা তখনই খণ্ডহর । আমার জন্মের পর আমি অবশ্য সে খন্ডহরও দেখিনি । সেখানে এখন ফ্ল্যাটবাড়ি । এই দ্বিস্হানিক ইতিহাসে বালক মলয় যেন বিনিময়যোগ্য বস্তুবিশেষ । ইমলিতলা, পানিহাটি, উত্তরপাড়া, আহিরিটোলা— সর্বত্রই তিনি “অন্যান্য”— অপর । প্রথমে ক্যাথলিক স্কুলে তারপর ব্রাহ্ম রামমোহন রায় সেমিনারিতে । কোন্নগরের আত্মীয়রা তাকে “খোট্টা খ্রিস্টান” বলে ডাকতেন—“ইমলিতলায় আমরা ছিলাম বঙ্গসংকর । মামারবাড়ি পানিহাটিতে গেলে খোট্টাসংকর।” মলয়ের চেতনা সদা সংকরায়িত জগৎ যেখানে ক্যাথলিক স্কুলের পিয়ানো টিচার মিস ডরোথির গায়ের পারফিউম ঘৃতকুমারী পাতার শাঁসের গন্ধের মতো ঠেকত বালক মলয়ের নাকে ।
এই আখ্যানে ইতিহাস আর কিংবদন্তিকে মিলিয়ে দিয়েছেন লেখক । ইতিহাস লোককথা ও মিথ নির্মাণে এক আত্ম-বিধ্বংসী জিরো-পয়েন্ট — ডায়াস্পোরার জিরো হিসট্রি বা ইতিহাসহীনতা । দেশ থেকে দেশান্তরে হস্তান্তরিত হতে থাকা উদ্বাস্তু জনগোষ্ঠী তার অতীত তথা সিকড়ের ইতিহাস থেকে উৎখাত হয় । এই মিথিক পরিসর ঔপনিবেশিকতার যুক্তিবদ্ধ প্রতর্কের বিরোধিতা করে । ইতিহাস এখানে শুধুই এক রেফারেন্স ফ্রেম যেন । গ্রন্হের শেষাংশে লেখক নিজেই একে লাতিন আমেরিকান ম্যাজিক রিয়ালিজমের সঙ্গে তুলনা করেছেন । তবে তাঁর উপনিবেশ বিরোধী অবস্হানের সাথে তাঁর জীবনেরও এক সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় । ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আক্রমণের সময়ে তাঁর পূর্বপুরুষরা সিরাজের পক্ষেই ছিলেন । সিরাজের পক্ষাবলম্বনকে ইমলিতলার বাড়িতে সাবর্ণ চৌধুরীদের “স্ট্র্যাটেজিক ব্লান্ডার” বলে মনে করা হত । ইংরেজদের বিরাগভাজন জমিদারবংশ এভাবেই ইমলিতলার ফেকলু ছোটলোক হয়ে ওঠে ।
সাবর্ণ চৌধুরী বংশের এই মিথিক ইতিহাস এক অসম্ভব বৈচিত্র্যের জাদুঘর — কপিলের দাদু ও তার ব্রাত্য হয়ে রকে খিস্তির টোল তৈরি, উত্তরপাড়ার সাবর্ণ ভিলার খণ্ডহরে ন’কাকিমার স্মৃতিতে ক্রন্দনরত ন’কাকা, আহিরিটোলার ঘনান্ধকার রান্নাঘরে রান্না করতে-করতে প্রঅয়ান্ধ পিসিমা –এই সব আধা বিশ্বাসগামী চরিত্রের চলাচল এখানে । পড়তে-পড়তে মনে হয় স্যামুয়ের জনসন থেকে ভিক্টিরীয় যুগ পর্যন্ত ঘনায়মান পরিবারকেন্দ্রিক “panoramic novel” ( এক ধরনের সমাজ ও সামাজিক গোষ্ঠীকেন্দ্রিক উপন্যাস )-এর কাঠামোকে তছনছ করে দিয়েছেন লেখক । বাংলা-বিহার মিলিয়ে জাতি-ধর্মের এক হাইব্রিড বুনোটে মলয়ের বেড়ে-ওঠা দেখতে পাই আমরা ; দেকি তাঁর ইন্দ্রিয়াদির উন্মেষ, নারীর প্রতি উদগ্রতার শারীরিকতার প্রকাশ । অনিশ্চিত যার জন্ম-ইতিহাস , সেই মেজদা বা বুড়োর বাড়িতে বেবুশ্যে মাগি আনা, হাত থেকে খিল পড়ে গিয়ে শব্দে ধরা পড়ে যাওয়া, মুন্সিজি-পত্নীর নগ্ন “সুডৌল গ্র্যানিট দেহ” আর দোলের রঙ মাখানোর মোচ্ছবের মধ্যেও শোনা যায় “মাসিক” হল “ম্যাজিক” শব্দের বঙ্গীয়করণ — ছোটোবেলাকার এক-দু গাছা বিধিনিষেধ । সংকরায়ণ কিন্তু আনপ্রহিবিটেড, অবশ্যম্ভাবী । তাই তো বন্ধনীমুক্ত হয় — ” এ হো ! কা হো ! আইভ্যান হো !
নখদন্ত
আমার পাঠের অনুক্রমে বছর পাঁচেক ফিরে গিয়ে ‘আওয়া ৪৯’ এর মে ২০০২ সংখ্যায় প্রকাসিত উপন্যাস ‘নখদন্ত : একটি পোস্টমডার্ন সাতকাহন’–এর দিকে নজর দি । শিরোনাম পড়ে আমার প্রাক-মলয় পর্বের গদ্য ধেকে একটা কথা মনে পড়ে গেল — “লোমচোখ”, যা তাড়া করে, ঠিক যেমন মলয় তাড়া করেন আমায় । ‘নখদন্ত’ আদ্যান্ত পোস্টমডার্ন আঙ্গিকে লেখা একটি সেল্ফ রিফ্লেকসিভ উপন্যাস, যেকানে রামায়ণের সাত কাণ্ডের নামে নামাঙ্কিত সাতটি দিনের ঘটনা হল ফ্রেম স্টোরি । এখানে পাওয়া যায় লেখক মলয় রায়চৌধুরীর ব্যক্তিগত ডায়েরি যেখানে তাঁর দাঁত মাজা, ওষুধ খাওয়া আর কমোদ পরিষ্কারে অযথা বিলম্বের পাশেই স্আন পায় তাঁর কাইনির নির্মাণসূত্র । লখনউতে মমতা অবস্হির আত্মহতভার খবর আর প্রতিবেশী সাধনবাবুর মৃত্যু একই বন্ধনী তৈরি করে, যার ভিতর থেকে উঠে আসে এক-এক করে পাঁচটি গল্প— “শেষ হাসি”, “শহীদ”, “জিরোনাম্বার মানুষ”, “ভাগ্য লিখনে হরফের দরকার নেই ” এবং “অট্টহাস্য অবিনির্মাণ” । এই পাঁচটি গল্প মলয়ের অথরিয়াল ফ্রেম ন্যারেটিভে বাঁধা, বাঁধা মৃত্যু আর হাসিতেও । আলাদা-আলাদা পত্রিকার জন্য লেখা এই গল্পগুলোর মধ্যে “অর্গানিক লিঙ্ক” আছে । একক ব্যক্তির ইতিহাস একানে নাযির যোগ । ধনতান্ত্রিক সমাজে মানুষের পণ্যায়ণ অদ্ভূত ভাবে প্যাসিভ এক ব্ল্যাক হিউমারে দেখিবে গেছেন মলয় । প্রথম গল্পে এলিজাবেথ জুটমিলের [ যেন এক নয়া ঔপনিবেশিক পরিসর ] মজুর কাঙ্গাল চামারকে পুলিশ যৌন অত্যাচারের মধ্য দিয়ে নিকেষ করে, তখন তার মুখের ঐ উদ্ভট হাসি দিবে শুরু হয় এই সিরিজ । ইংরেজদের আগে পাট আর জুটের চাষ, উপনিবেশে আর উত্তরউপনিবেশে পাটকল, জুটমিল, সেখানে ইউনিয়নের দলাদলি, মজুরদের আত্মহত্যা, কলের রেজিস্টারে নাম না থাকা “জিরো নাম্বার শ্রমিক”— এইসব নিবেই মলয়ের আন্ধার পোলিটিকাল কনটেন্ট । উপস্হাপনা ও বিবরণ যত তীক্ষ্ণ, ততই নির্ভার ও আবেগহীন । মলয় ঠিক ট্যাজেডি লিখতে চাননি । পাতাজোড়া বন্ধ কারখানা ও আত্ম্ত্যা-করা শ্রমিকদের নামের তালিকা, চটকলগুলোতে স্বাধীনতার আগে-পরে মালিকানার হাতবদলের পাতার পর পাতা লিস্টি— সংখ্যা এবং তথ্য এখানে স্বয়ম্ভর ; রেফারেন্সিং রাজনৈতিক রিপোর্টের আবহ তৈরি করেছে । কাঙ্গাল চামারের পোঁদে গোঁজা রদ থেকে গান ভেসে এসেছে– “জোর কা ঝটকা ধিরে সে লগে” । রাজপুত কন্সটেবলের মৃত্যুতে অভিযুক্ত কাঙ্গাল চামার হাপিশ হয়ে যায় । পরের গল্পে ঐ একই জুটমিলের পে ক্লাকফ সত্য আচাজ্জির আত্মহত্যা এক স্বঘোষিত শহীদত্বের বাচন । শহীদত্ব কি স্বয়ম্ভর ? নাকি শহীদ হতে গেলে নির্ভর করতে হয় অপরের ওপর ? তারপর আসে থার্ড সিরিজ— কাঙ্গাল চামারের পরিবর্তে দুই অস্তিত্বহীন “জিরো নাম্বার ওয়ার্কার” খালেদালি মণ্ডল ও বৈকুন্ঠ সুর । সিমাহিন দারিদ্র, ক্ষুধা, শেষে ভিক্ষার কলকাতায় খালেদালি মণ্ডলের মৃত্যু । তাও যেন শান্তি নেই । মর্গ থেকে দেহের অদলবদল —খালেদালির জায়গায় হিন্দু শরীর — দিবাকর যুগি । ডেডবডির ধর্ম নিরুপণে মলয়ের জিরো নাম্বার ভারতবর্ষে এ যেন নিকেষ ও হাপিশে এক চৈত্র সেল — “খালেদালি মণ্ডলের দেহ গেল কোথায় স্যার ? এই দিবাকর যুগি লোকটার দেহ আর আইডেনটিটি দুই-ই আছে । কলকাতার মর্গে যে লোকটার দেহ আছে তার কিন্তু আইডেনটিটি নেই । আর খালেদালি মন্ডলের দেহও নেই আইডেনটিটিও নেই । জিরো ? অ্যাঁ ?”
ফোর্থ সিরিজ খালেদালির ছেলে আমিনুলের চাকরির খোঁজে কলকাতায় আসা । মাথায় টাইপরাইটার চড়ানো বেকার যুবকদের ভাগ্য পরীকআ মলয়ের চোখা বিদ্রূপ, যা প্রতীকী সংবাদ ও কথপোকথনে সমসময়ের এক সিরিওকমিক ছায়া হয়ে যায় । টাইপ রাইটারবাহীরা গেয়ে ওঠে —“হুমহ না ভাই হুমহু না” — ( সলিল চৌধুরীর সুরে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া সুকান্ত ভট্টাচার্যের ‘রানার’ কবিতাটির প্রয়োগ ) । “খপোধ বাড়ে” “রোদ বাড়ে” “ক্লান্তি বাড়ে” আর তারই সঙ্গে লাইনও ।
শেষ গল্পে কাঙ্গাল চামারের মরণোত্তর হাসি মিশে যায় শহরের পার্কে সক্কাল বেলায় আমলাদের লাফিং প্র্যাকটিসের সাথে । দেখতে থাকে অর্ণব । বৃষ্টিভেজা ঐ সকালে গোগ্রাসে পড়ে ফ্যালে স্বাধীনতা দিবস অনুষ্ঠানে বিভ্রাটের খবর । পতাকা উত্তোলনের সময়ে পতাকাটি না খুলে দণ্ডের ওপর থেকে পুঁটলিসহ মুখ্যমন্ত্রীর পায়ের সামনে এসে পড়ে । অনুষ্ঠান অবশ্য চলতে থাকে । পরে জানা যায় পাটের দড়ি দিয়ে কাঠের কপিকলে বাঁধাতেই এই বিপত্তি । স্বাধীনতার ঐ পতাকাহীন দণ্ড কাঙ্গাল চামারের যৌনাঙ্গ হয়ে ওঠে, যার বীর্য ও রক্তে চকমক করছিল পুলিশের বুট । পতাকাহীন ঐ দণ্ড সহাস্য ক্যাসট্রেশানের প্রতীক হয়ে ওঠে । এই হল মলয়ের উত্তরঔপনিবেশিক ভারতবর্ষ যেখানে দেশভাগের মানদণ্ড বলতে বোঝায় নুনুর খোসা— ছাড়ানো, অথবা না-ছাড়ানো । তাই কথনের কিনারায় আবার শোনা যায় প্রপাত-সংকেতের মত ঐ হাসি, ঠিক যেন বাখতিনীয় কার্নিভাল লাফটার ( রুশ দার্শনিক মিখাইল বাখতিন হাসিকে বিপ্লবী রদবদল ঘটানোর হাতিয়ার মনে করেন ), যা নিতান্তই অশান্তিকামী ও রাজনৈতিক ।
“নখদন্ত”-র ফ্রেম ন্যারেটিভে লেকক-প্রতিস্বের এক অনর্গল নিমফাণ চকলতে থাকে । মলয় কী বই পড়ছেন, কী করছেন, কী দেখচেন —কোন যাপন ও পাঠ অভিজ্ঞতা থেকে আদল পাচ্ছে তাঁর কাহিনিরা— এসব যেমন আছে, তেমনই আছে প্ররোচনামূলক নানা বভক্তিগত পোলেমিক । শঙ্খ ঘোষ থেকে সন্দীপন চট্তোপাধ্যায়— এসট্যাবলিশমেন্ট ও আপোষের প্রতি তীব্র শ্লেষ । উল্লেখযোগ্য ফ্রেম স্টোরি জুড়ে “Notes” নামক অংশগুলি, যেকানে বাংলা ্রফে ইংরাজি ভাষায় নানা অ্যাফরিজম পাওয়া যায় । ট্রান্সলিটারেশন পাঠ অভিজ্ঞতাকে মোচড় দেয় । যৌক্তিক সামান্যিকৃন প্রক্রিয়ায় লেকক এক বিমূর্ত এবং প্রাব দার্শনিক স্পেস তৈরি করেন উপনভাসটির ভিতর, উদাহরণস্বরূপ — ” নাথিং ইজ টু মিন ফর ইম্যাজিনেশন অ্যাজ নাথিং অন আর্থ ইজ ইনসিগনিফিক্যান্ট” । উপন্যাসটিতে মলয় নিজেই “ঋদ্ধ” আর “মুগ্ধ” হওয়ার মধ্যে ফারাক করেন । মলয় মুগ্ধ নয়, ঋদ্ধ হতে চান । আর আমরা ?
অরূপ তোমার এঁটোকাঁটা
আমি যখন মলয় রায়চৌধুরীর উপন্যাস পড়িনি তখনও আমি মলয়কে আর মলয় আমাকে পড়ছিলাম । পড়েই যাচ্ছিলাম । ‘ডুবজলে যেটুকু প্রশ্বাস’ পড়তে গিয়ে নোট পরীক্ষক অতনুকে দেখলাম পচাছেঁড়া নোটের ধড়পাকড়ের ভিতর বসে বসে পোড়া নোটের গন্ধকে মানুষের পোড়া মাংসের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে, আমার মনে পড়ল বছর দুয়েক আগে লিখতে শুরু করা এযাবৎ অসম্পূর্ণ আমার উপন্যাসের প্রথম দুটি লাইন — ” মৃত্যুর মত দশ টাকার কয়েন । মৃত্যুর যত দশ টাকার কয়েন ।”
‘এই অধম ওই অধম’ পেরিয়ে মলয়ের ট্রিলজিতে হাত দিয়েছি, একদিন পড়ন্ত বিকেলে সোমানাথদার ( সম্পাদক : অপর ) টেলিফোন ও এই লেখার অবতারণা । তারপর ফেসবুকে মলয়দার সাথে কথা, ই-মেল চালাচালি । তাঁর ও তাঁর দাদা সমীর রায়চৌধুরীর সাহায্যে কলেজ স্ট্রিটের আনাচে-কানাচে হাতে-হাতে হাতেনাতে পাওয়া মলয়দার উপন্যাস, গল্প ও প্রবন্ধমূলক গদ্য ।
সবই মলয়ের কথামত । যেমন ‘হাওয়া-৪৯’কে দেওয়া ইনটারভিউতে তিনি বলেন— ” আমার বই তো গাদাগাদা বিক্রি হয় না, কোনো ফিক্সড পাবলিশারও নেই । পড়তে হলে বইটা খুঁজে খুঁজে জোগাড় করতে হয় ; অর্থাৎ , আমার বই যিনি পড়েন বাধ্য হয়েই পড়েন, পড়তেই হয় বলে পড়েন ।” আমিও তেমনই এক শ্রমিক-পাঠক । অন্বেষণের কায়িকতায় পাঠ প্রক্রিয়ার সম্প্রসারণ ও বিয়োজন দুইই ঘটে । খোঁজা ও পড়ার এই গল্পে উত্তরপাড়া শহরতলির সহস্মৃতি শেয়ার করি আমরা দু’জন । এই স্হানিক এককত্ব মলয়ের আখ্যানে এক কূটাভাস হয়ে দেখা দেয় যখন ইমলিতলার অন্ত্যজ পাড়ার জন্মস্হান বা উত্তরপাড়ার সাবর্ণ রায়চৌধুরীর বিলীয়মান ঐশ্বর্য — এইসব গম্বুজ পাশ কাটিয়ে মলয়ের কাহিনীগুলি ধারণ করতে থাকে অন্তর্দেশীয় প্রবাসের এক নব্য-বাঙালিয়ানাকে, যা দোআঁশলা, বহুভাষিক, বহু-সাংস্কৃতিক ও অধুনান্তিক সমাজ ভাবনার্ দোসর । এই সব শাখা-প্রশাখা থেকে ফিরে তাকালে শিকড়ের গম্বুজস্বরূপ ইমলিতলা বা উত্তরপাড়ায় এন অনাবিল তরলতা তৈরি হয় । মলয়ের আখ্যান এই ” Space of Flows” [ পরিসর যখন সদা ধাবমান, একক অবস্হান নয় ] এর স্মৃতিবাহী ।
শ্রমসাধ্য প্রাপ্তি দিয়েই শুরু করি । ‘বিষয়মুখ’ পত্রিকার ২০০৭ জুলাই – ডিসেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত উপন্যাস ‘অরূপ তোমার এঁটোকাঁটা’ পড়তে-পড়তে যে পেনসিল দিয়ে মার্ক করছিলাম, দেখলাম সেটার শিষটা ভাঙা । তারপর ঐ এঁটোকাঁটা শিষ দিয়েই মার্ক করা শুরু করলাম । এই ‘এঁটোকাঁটা’ মধ্যবিত্ত ভেতো বাঙালির মুখোশ-উচ্ছিষ্ট যেন । উৎকৃষ্ট এবং উৎ-সৃষ্ট । পিতামহ-মাতামহের গুপ্ত যৌনজীবনের এঁটোকাঁটা । প্রয়াত দাদুর চিঠি-চাপাটি দিয়ে শুরু এই খনন । টেক্সট যেন এক খননায়ন — চোরাগোপ্তা খুলামকুচি আমদানি করে । সাধু বাংলায় লেখা অতীতের হলুদ ন্যারেটিভ জাক্সটাপোজড হয় প্রজন্মান্তরের ই-মেল বা চ্যাট-এর সঙ্গে । কাহিনির প্রবাহ বেনারসে, শিকড় বর্ধমানে । ইন্দিরা ব্যানার্জির প্রয়াত দাদু অতুল মুখোপাধ্যায় বা “অতুল মূর্খ”র বন্ধু শিশির দত্তর লেখা যে ন্যারেটিভ মলয়ের উপন্যাসের মেরুদণ্ড, তা এক জটিল বহুকথন সম্বলিত প্যালিম্পসেস্ট । শিশির দত্তর সাধু বাংলার ওপর পাঠিকা তথা কাইনির অন্যতম প্রধান চরিত্র কল্যাণী/কেকা বউদির ন্যারেটোরিয়াল প্রেজেন্স । তার ওপর আবার নির্মলবাবুর ( অতুলের বন্ধু ) বাবা, যার ডায়েরিতে শিশির লিখেছিলেন এই কাহিনি, তাঁর প্রফেসোরিয়াল নোটস — লেককের বিমূর্ত ও তাত্ত্বিক পরিসর ; এই ত্রিস্তরিত আখ্যানের সমান্তরাল চলে লিখন আর পাঠ । শিশির পড়েন বন্ধুর বাবা তথা প্রফেসরের সমাজভাবনার র্যানডাম নোটস, আর তারই ওপর লিখে ফ্যালেন নিজের বৈদেশিক যৌন কাহিনি । অন্যদিকে কেকা বউদি, যিনি নিঃসন্দেহে মলয়ের উপন্যাসের র্যাডিকাল নায়িকা, তিনিও তো শিশির কাহিনির পাঠিকাই । তবে শিশিরের মতন তিনিও লেখা ও পাঠ দুই করে থাকেন । শিশিরের কাহিনিকে ক্রমাগত আন্ডারকাট করতে থাকে কেকা-কথনের বলনকলা ।
ইমপোটেন্ট ও বধুনির্যাতনকারী প্রসন্নকান্তির বিদ্রোহিনী স্ত্রী কল্যাণী পাড়ার ছেলে অতুলের সাথে বেনারস পালিয়ে আসেন । সেখানে অতুল আর কল্যাণী তথা নামান্তরে কেকা শুরু করে গাঁজাচরস আফিমের ব্যবসা — “দ্রুত ধনী হবার ব্যধি” । বেনারসের মন্দির চত্ত্বরে কালো গ্র্যানাইটের ফ্যালিক এক লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে কেকা । কিন্তু ক্রমশই অতুলের কাছে কেকার শরীর আকর্ষণ হারায় আর অতুল লিপ্ত হয় অন্য-অন্যান্য নারীশরীরের সাথে । মার্কিনী জোসেফিনের সঙ্গে শয্যা আমদানি করে হাইব্রিড এক শিশুপুত্র ‘কং’ । ‘কং’কে প্রতিপালনের দায় পড়ে কেকার ওপর । জোসেফিন তখন উধাও । শিশিরের কাহিনির সিংহভাগ জুড়ে থাকে কেকার ভাষায় “কভাবলা কামুক”টার সাথে ভাইকিং রমণী ম্যাডেলিন ক্যরিয়েটের সঙ্গম-লীলা । সাধু ভাষার মোচড়ে বলা এই যৌন আখ্যান পর্নোগ্রাফি আর এসক্যাটোলজির মধ্যিখানে থেকে যায় । কখনও তা প্লেজার দেয়, কখনও কুন্দেরায়েস্ক এক বিষাদ । এক অতলান্ত অনুভব । অ্যাটলান্টিকের এপার থেকে ওপার— সংকরায়ণের গন্ধ এই শরীরময় এঁটোকাঁটায় । মলয়ের বর্ণনাগুণে এই ইনটারকোর্স মিস্টিক এক রিচুয়ালে পরিণত হয় — “অগরু” এবং “কান্তা” নামে ছয়টি করে শিশির তরল প্রলেপ সূর্যাস্তের পর ফোরপ্লের ফোরগ্রাউন্ড তৈরি করে । শিশিরের এই ‘বিদকুটে’ সাধু বাংলা কি তবে রক্ষণশীল এক ভাষা-পদক্ষেপ, যেমনটা কেকা বলে — “আর লিখলি তো লিখলি এই বিদকুটে বাংলায় কেন ? সোজা বাংলায় লিখতে গেলে নোংরা করে ফেলতিস ?” শিশির তথা ‘শিশু’ আর ম্যাডেলিন তথা ‘ম্যাডি’র শরীর যেন ভাইকিং রাজগৌরবের এক ঐতিহাসিক যুদ্ধক্ষেত্র । স্ক্যান্ডিনেভিয় নৌযোদ্ধাগণের বংশজ অতিকায় ম্যাডেলিন ও শিশিরের এই সঙ্গমে নারী সরীর প্যাট্রিয়ার্কাল গেজের নিষ্প্রাণ পাঠবস্তু নয় । তা এক ঋদ্ধ ইতিহাসমুখরিত চিহ্ণ, যা তেরছা করে দ্যায় যৌনতার পুংশাসিত কাঠামোকে । পুরুষ হেথায় নারীর বশিকৃত ক্যাবলা-কামুক মাত্র । ম্যাডেলিন চলে যাবার পর চাবুক আসে কেকাবউদির হাতে, যখন তিনি সিডিউস করেন শিশিরকে । বিদেশি গান বদলে যায় বৈজয়ন্তীমালার “হোঁটোপে অ্যাইসি বাত”-এ । এই সিক্রেটই কেকার সম্পদ — ” আমার গায়ের রঙ আহ্লাদী পুতুল ম্যাডেলিনের মতন নয়, তাতে কী । আমি এমন অপ্সরা যার মুঠোব আছে শকুনির পাশা । মুকখু চাষা শিশির কিছুই আঁচ করতে পারেনি । ম্যাডেলিনের শেখানো এলকুমি-বেলকুমিই পুঁজি ।”
কেকার অভিসন্ধিতে শিশির এক অনুঘটক মাত্র । শিসির-কেকার শয্যা থেকে উঠে আসে ‘বং’ । কেকা হন কং-বং-এর মা — “অতুল আমার কোলে ওর বাচ্চা কংকে ধরিয়েছে । আমি ওর কোলে শিশিরের বাচ্চা বংকে ধরাব ” এই ধরাধরির গুপ্ত পারিবারিক ইতিহাস ছুঁয়ে যায় বারানসীর সাংস্কৃতিক ইতিহাস– অবাধ ফ্যাগের সন্মোহন থেকে বজরং দলের উপস্হিতি যারা তুকটাক চুমুকেও আস্ত রাখেনি । এই আখ্যান শেষ হয় অতুলের নাতনি ইন্দিরা ও শিশিরপুত্র সুবীরের প্রণয়-পরিণয় দিয়ে । তারা গুপ্ত ইতিহাস সম্বলিত ডায়েরিটিকে চুপচাপ স্বস্হানে রেখে দেওয়াই সাব্যস্ত করে । টেক্সটের অপেক্ষা শুরু হয় আবার পাঠ ও লিখন বৃত্তের ভিতর ঢুকে পড়ার জন্য । শিশির জানে সে মোহরা । কেকার । কেকা অতুলের মৃত্যুতে কাঙালিভোজন করিয়ে মাদার ইন্ডিয়া সাজে । মলয়ের উপন্যাসে যৌনতা অস্তিত্ব তথা আইডেনটিটিরই বিনির্মাণ ঘটায় । শিশির-কেকারা বুঝতে পারে কত-কত আরও কত-কত শিশির-কেকাদের তারা তাদের শরীর-মন আর অস্তিত্বে পুষছে । লেখক মলয় তার ডিসকার্সিভ স্পেস তৈরি করেন নির্মলের অধ্যাপক পিতার ‘জ্ঞানবাক্যের’ পরিসরে । তাঁর ডায়েরিতেই তো লেখে শিশির । তাঁর সফল দার্শনিক অ্যাফোরিজম এক সমান্তরাল প্রাতর্কিক পরিসর নির্মাণ করে — এক প্রফেটিক স্পেস যার বয়ানে বাঙালির দোআঁশলা আধুনিকতায় এক উনিশ শতকীয় অ্যনাক্রনিস্টিক অধুনান্তিকতার রিপোর্ট পাওয়া যায় । সেখানে উঠে আসে উত্তর-উপোনিবেশের অনুসঙ্গ, ভালো-মন্দের নৈতিক বিচার ও সর্বোপরি এই ‘আমি’র আবরণ— “আমি নামক নিবাসটি যে যাবতীয় সমস্যার আগার । তাকে সংজ্ঞায়িত করা অসম্ভব । কতরকম আমি যে আছে— সবই অনির্ণেয়, তার ইয়ত্তা নেই । পার্শ্বচরিত্র নির্মলের প্রয়াত পিতা যেন ‘অরূপ তোমার এঁটোকাঁটা’র অধুনান্তিক ডেড অথর — স্বয়ং মলয় রায়চৌধুরী । শিষ বড্ডো ছোটো হয়ে গেছে, পড়াও শেষ । শিশির আর কেকার মত আমিও পড়লাম আর লিখলাম ।
 মারুফুল আলম | 27.58.255.50 | ১১ আগস্ট ২০২১ ১১:৩৬734859
মারুফুল আলম | 27.58.255.50 | ১১ আগস্ট ২০২১ ১১:৩৬734859মারুফুল আলম নিয়েছেন মলয় রায়চৌধুরীর সাক্ষাৎকার
মারুফ :যদিও এখন আমরা এসব আর কেউ কাউকে জিজ্ঞাসা করি না–তবুও বলি,এখন এই তীব্র সময় বা অসময়ে সবমিলিয়ে কেমন আছেন?
মলয় : বেশ কোনঠাশা হয়ে আছি ।
মারুফ :পাটনাতেই তো লেখালেখি শুরু হয়েছিল?প্রথমে কি লিখেছিলেন– গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ নাকি অন্যকিছু?
মলয় : ইতিহাসের দর্শন নামে একটা ধারাবাহিক লেখা : বিংশ শতাব্দী পত্রিকায় ।
মারুফ :লেখালেখি শুরুর আগেও তো নানা রকম পড়ালেখা করেছেন–সেই 'পাঠ পর্যায়' সম্পর্কে কিছু জানাবেন কি?
মলয় : প্রথমে ক্যাথলিক স্কুলে পড়তুম । সেখানে ফাদার হিলম্যানের কাছে ওল্ড আর নিউ টেস্টামেন্টের ঘটনা জানলুম । তারপর, রামমোহন রায় সেমিনারি ব্রাহ্ম স্কুলে পড়তে গিয়ে গ্রন্হাগারিক নমিতা চক্রবর্তীর ওসকানিতে ব্রাহ্ম লেখক আর কবিদের পড়া আরম্ভ করলুম। দাদা সমীর রায়চৌধুরী কলকাতায় সিটি কলেজে পড়তেন আর আসার সময়ে তিরিশের দশকের কবিদের বই আনতেন । পাটনায় বাবা বই কিনে দিতেন । যাকে বলে বুকওয়র্ম, তাই ছিলুম।
মারুফ :আপনার প্রথম বই 'শয়তানের মুখ' না 'মার্কসবাদের উত্তরাধিকার' – কোনটি? 'শয়তানের মুখ' তো 'কৃত্তিবাস'ই করেছিল–সেই সময়ে বইটি সাড়াও ফেলেছিল বেশ।তারও পরে 'হাংরি আন্দোলন'–তাই তো?তো,ব্যাপারটি এমন নয় যে,চসার,স্পেংলার বা অন্য কেউ তা ঘটিয়ে দিল,নিশ্চয়ই প্রস্তুতিটা ছিল—তা এই যে 'হাংরি আন্দোলন' তার প্রস্তুতি এসবের অনুপ্রেরণার উৎস কি?
মলয় : প্রথম বই ‘মার্কসবাদের উত্তরাধিকার’ । ছোটোলোক অন্ত্যজদের ইমলিতলা পাড়ায় শৈশব-কৈশোর কেটেছিল আর ওই পাড়াটাই ছিল প্রস্তুতির বনেদ । আমার ছোটোলোকের ছোটোবেলা, ছোটোলোকের যুববেলা, ছোটোলোকের শেষবেলা বইগুলো পড়লে ব্যাপারটা বুঝতে পারবে । সুনীল গাঙ্গুলি শয়তানের মুখ বইটার প্রকাশক ছিলেন, কিন্তু সাড়া ফেলতেই অস্বীকার করতে থাকেন । তারপর আমারিকায় কবিতা লেখা শিখতে গিয়ে সেখান থেকে আমাকে হুমকি দিয়ে চিঠি লিখতেন । ইমলিতলার অন্ত্যজদের জীবন আর পঞ্চাশ দশকে কলকাতায় উদ্বাস্তুদের দুর্দশা কাজ করেছিল সুতলিতে আগুন ধরাবার ।
মারুফ :সাহিত্যের বহুল আলোচিত 'হাংরি মুভমেন্ট' সম্পর্কে আজ এই এতোকাল পরে যদি অতি সংক্ষেপে আপনার মতামত জানতে চাই–তো কি বলবেন?
মলয় : কিংবদন্তির ব্যাখ্যা হয় না, আন্দোলনটা ছিল গ্রিসের ইউলিসিসের মতন সবকিছুর বিরুদ্ধে লড়াইও করে লক্ষে পৌঁছোনোর ব্যাপার ।
মারুফ :আপনার এক বাক্যে লিখিত দু'টি নভেলার একটি 'ভিড়পুরুষ ও নরমাংসখোরদের হালনাগাদ' এর শেষটা একটা অভিনব সমাপ্তি। ফিল্মিক যবনিকাপাত। বেশ্যাপাড়ার একটি ঘরে গিটার বাজিয়ে পতিতারা সমবেত কণ্ঠে একটি ইংরেজি গান গাইছে। এ নভেলায় ১৯৭১-এ পাকবাহিনীর নির্যাতন,স্বাধীন দেশে মৌলবাদের উত্থান এবং অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদের নিহতের ঘটনার উল্লেখ আছে।বিরামচিহ্নহীন এ লেখার প্রেরণা এবং আইডিয়া আপনি কিভাবে পেলেন?
মলয় : লিখতে-লিখতে আপনা থেকেই ঘটে গিয়েছিল ।
মারুফ :'অরূপ তোমার এঁটোকাঁটা' উপন্যাস লেখার ভাবনার কথা জানতে চাচ্ছি। এরকম দুঃসাহসিক আখ্যান তীর্থস্থানে নেশা ও যৌনতাময় ক্যাওস নিয়ে টেক্সট আমাদের পাঠ অভিজ্ঞতায় একটা অনন্য পাঠকৃতি।বাংলা উপন্যাসের টেক্সটে আপনার বাক্য নির্মাণ,ভাষাগত দিক ও উপন্যাসটি রচনার পুর্ব প্রস্তুতি নিয়ে কিছু বলুন।
মলয় : বেনারস আর কাঠমাণ্ডুতে হিপি কলোনিতে কয়েকমাস সময় কাটিয়েছিলুম । সঙ্গে ছিল আমার পেইনটার বন্ধুরা । সেই অভিজ্ঞতা থেকে লিখেছি । আমার বেশিরভাগ উপন্যাস নিজের জীবনের ঘটনা থেকে সংগ্রহ করা । পেইটারদের মতন এই উপন্যাসে আমি ফ্রেম থেকে বেরিয়ে জীবনকে আঁকতে চেয়েছি, সব রকমের রঙসুদ্দু ।
মারুফ :'ডুবজলে যেটুকু প্রশ্বাস' থেকে 'জলাঞ্জলি' 'নখদন্ত' হয়ে 'একটি নিরুপন্যাস'–এগুলো শুধু বিচিত্র আখ্যান নয়।ভিন্ন ভিন্ন নির্মাণ পদ্ধতিও বটে।আখ্যানের সাথে সাথে পৃথক টেকনিকের এপ্লিকেশন বা আইডিয়াও কি মাথায় রেখে লিখতে থাকেন?আপনার নিজের প্রস্তুতিটা একটু বলুন।
মলয় : হ্যাঁ । একটা উপন্যাস লেখার মশলা যোগাড় হয়ে গেলে তার আঙ্গিক নিয়ে ভাবি। চেষ্টা করি যাতে কমার্শিয়াল লেকখদের মতন একই ভাষা আর আঙ্গিক না হয়ে যায় ।
মারুফ ।আপনি খুব সচেতন লেখক,সবার সাথে পংক্তিভোজে আপনাকে দেখা যায় না।সেজন্য লেখকদের প্রতি একটা সমীহবোধ পাঠকদেরও থাকে।কিন্তু একটা কমন টেন্ডেন্সি হলো ওই লেখকগণই যখন বাংলাদেশে কোথাও লেখেন তখন তাঁর এই রুচি,বাছ-বিচারটা অটুট থাকে না।লিটলম্যাগাজিন বা উৎকৃষ্ট সাহিত্য পত্রিকা নয়,একেবারে ঈদ সংখ্যায় বাংলাদেশের তৃতীয় শ্রেণির ট্রাশ লেখকদের পাশেই লেখেন।এটা কেন হয় বলে আপনি মনে করেন?
মলয় : ভারতে বসে টের পাওয়া যায় না কোনটা ঈদের আর কোনটা মৌলবাদী নয় । যারা মৌলবাদী নয় তারাও দাড়ি রাখে । এই যেমন তুমি ; আমি কেমন করে জানবো তুমি মৌলবাদী কি না । হুমায়ুন আহমেদকে বাংলাদেশে গুরুত্ব দেয়া হয়, আমি দিই না । তবু ওনার লেখা যে পত্রিকায় বেরোয় তাতে লিখেছি । বাংলাদেশের তরুণীরা আমাকে তাঁদের কবিতা পড়তে বলেন ; তাঁরা গোঁড়া মতবাদের বা কাব্য-প্রতিভার চিন্তা করি না ; সুন্দরী হলেই হলো ।
মারুফ :বাংলাদেশের সাম্প্রতিক কথাসাহিত্য চর্চা সম্বন্ধে আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন।এ বিষয়ে আপনার পাঠ অভিজ্ঞতা জানতে চাইছি।
মলয় : এখন আর তেমন পড়ি না ; বইপত্র পাই না । তবে ইনটারনেট থেকে টের পাই যে নানারকমের বাঁকবদল ঘটে চলেছে, ভাষায়, আঙ্গিকে, বিষয়বস্তুতে, ভাবনায় । আমি তো মুনিরা চৌধুরীর কবিতা প্রথমবার পড়ে স্টানড হয়ে গিয়েছিলুম ।
মারুফ :আপনার 'নামগন্ধ' শুরুই হচ্ছে পাঠক চেতনায় একটা ভায়োলেন্স তৈরি করে।উপন্যাসের আখ্যানের প্রথাগত টেকনিক আপনি ভেঙে দিয়েছেন। এটা তো শুধু টেকনিক না,এর পেছনে কোন সাংস্কৃতিক চেতনা ক্রিয়াশীল,যা থেকে আপনি এটা করেন?
মলয় : ওটা সত্যিকার ঘটনা, দেখেছি, তাই মানসিক আক্রমণটা কাজে লাগিয়েছি। চাকুরিসূত্রে আলুচাষিদের দুর্দশা দেখেছি, সেগুলো কাজে লাগিয়েছি । বলা যায় যে আমি যাদের দুর্দশা নিয়ে লিখি তাদের দুর্দশা হয়ে ওঠে টেকনিক । বইয়ের শেষটা আপনা থেকে মাথায় এসে গিয়েছিল। শেষটা মাথায় আসার পর রিভাইজ করার সময়ে অনেক ঘটনা আর নামধাম পালটে দিয়েছিলুম।
মারুফ :সুবিমল মিশ্রের সাহিত্য কীর্তি নিয়ে আপনার মূল্যায়ন কি? দেবেশ রায়?
মলয় : সুবিমল মিশ্র অসাধারণ লেখক ; দেবেশ রায়কে কম পড়েছি । তিস্তাপারের বৃত্তান্ত পড়িনি।
মারুফ :সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে আপনি নিজেও তৎপর।বর্তমান চলমান ধারায় শিল্পসাহিত্যের কিছুটা প্রতিফলনও সেখানে ঘটেছে।ওয়েবজিন,ইবুকও ইতোমধ্যে চলে এসেছে।অনেকেই শুধু ফেসবুক ব্যবহারকারী সাহিত্যিক।আবার অতিসামান্য দু'একজন যেমন 'প্রতিশিল্প' সম্পাদক অভাজন এই আমার ধারণা,ফেসবুক নানান চর্চা সহ সাহিত্য চর্চায়ও দ্রুত 'মেইনস্ট্রিম'ই হতে যাচ্ছে।তাছাড়া ফেসবুকও তো পুঁজি এবং অন্যান্য বিবেচনায় শেষ পর্যন্ত একটি প্রতিষ্ঠানই,নয়? সার্বিকভাবে এইসব বিষয়-আশয় আপনি কীভাবে দেখেন?
মলয় : আমরা পাঠকের কাছে কেমন করে পৌছোবো ? আমার বই তো বাংলাদেশে এখন কয়েকটা গেছে ; প্রকাশক পাচ্ছি । ইনটারনেটের সাহায্যে পাঠক জানতে পারছেন আমাকে। তার আগে সবাই জানতো প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার-এর কবি হিসেবে ।
মারুফ :উপন্যাসের তুলনায় ছোটগল্প এতো কম লিখলেন?
মলয় : সত্যি কথা । লিখলে কোথায় দেবো সেটা একটা বড়ো ব্যাপার । অনেকে আমার লেখা ছাপতে চাইতো না । ফলে আগ্রহ হতো না । যে ছোটোগল্পগুলো লিখেছি তা সবই পরিচিত সম্পাদকদের পত্রিকায়।
মারুফ :সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর কথাসাহিত্য নিয়ে আপনার অভিমত কি?
মলয় : ওনার সম্পর্কে বলতে হলে যে উচ্চতার দরকার, আমি সেই তুলনায় অত্যন্ত ক্ষুদ্র ।
মারুফ :ছোটলোকের ছোটবেলা, ছোটলোকের যুববেলা,এই অধম ওই অধম– এসবই আত্মজীবনীমূলক।তারপরও কি আপনি আত্মজীবনী লিখবেন?
মলয় : লিখেছি তো ! ছোটোলোকের শেষবেলা । ইনটারনেটে পাবে ।
মারুফ :'কবিতীর্থ' আপনার ৩টা নাটক দিয়ে নাটকসমগ্র বের করেছিল।নাটক আর লিখবেন না? ১৯৬৩-তেই প্রথম নাটক – 'ইল্লত' লিখেছেন। বাংলাসাহিত্যে আপনার পছন্দের নাট্যকার কারা?
মলয় : না, নাটক আর লিখিনি । তবে চারটে কাব্যনাট্য লিখেছি ।
মারুফ :বাইরের দেশের কার কার লেখা আপনার কথাসাহিত্য চর্চায় প্রণোদনা দিয়েছে বলে আপনি মনে করেন।প্রভাবিত হওয়ার কথা বলছি। এমন মনে হয় আপনার?
মলয় : আমি বুকওয়র্ম হবার দরুন শেকসপিয়ার থেকে মুরাকামি সবই পড়েছি । তাই বলা কঠিন ।
মারুফ :আপনার একটা বই প্রকাশিত হয়েছে। যেখানে আপনি নিজেই নিজের ইন্টারভিউ নিয়েছেন।এটা একটা বিরল ঘটনা। আপনি কোন মন্তব্য করতে চান? এটা কি নিজের সাহিত্যের সারবস্তু,নিজের শিল্পদর্শন,নিহিত ভাবনাসকল অন্য কেউ ঠিকমতো অবতারণা করতে পারবে না বুঝে নিজেই প্রশ্ন এবং নিজেই উত্তর করলেন?
মলয় : সম্পাদকের অনুরোধে ঘটেছিল । আমিও সুযোগটা নিলুম, নতুন ধরণের ব্যাপার বলে ।
মারুফ :একটু জানতে চাইছি,আপনার সবচে' উল্লেখযোগ্য 'ডুবজলে যেটুকু প্রশ্বাস' আপনি কতোদিনে শেষ করেছিলেন?
মলয় : ওটাই আমার প্রথম উপন্যাস । বেশ সময় লেগেছিল । বছর খানেক তো হবেই ।
 মলয় রায়চৌধুরী | 27.58.255.50 | ১১ আগস্ট ২০২১ ১১:৫১734860
মলয় রায়চৌধুরী | 27.58.255.50 | ১১ আগস্ট ২০২১ ১১:৫১734860অভিশপ্ত কবিরা - ভেরলেন, রেঁবো, মালার্মে, করবিয়ের প্রমুখ : মলয় রায়চৌধুরী
‘পোয়েত মদি’ ( Poète maudit ) বা ‘অভিশপ্ত কবি’ নামে ১৮৮৪ সালে ফরাসি প্রতীকবাদী ও ‘ডেকাডেন্ট’ কবি পল ভেরলেন একটি বই প্রকাশ করেছিলেন । অভিধাটি ১৮৩২ সালে প্রথম ব্যবহার করেন অ্যালফ্রেদ দ্য ভিনি ( Alfred de Vigny ) তাঁর ‘স্তেলো’ উপন্যাসে ; তিনি বলেছিলেন ‘পোয়েত মদি’ হিসাবে চিহ্ণিত লোকগুলোকে জগতের ক্ষমতাধর মানুষেরা চিরকাল অভিশাপ দেবে। ত্রিস্তঁ করবিয়ের (Tristan Corbière ) , জাঁ আর্তুর র্যাঁবো, স্তেফান মালার্মে, মারসেলিঁ দেবোর্দে-ভামো ( Marceline Desbordes-Valmore ) এবং আগুস্তে ভিলিয়ার্স দ্যলিজলে আদঁকে ( Auguste Villiers de l'Isle-Adam ) পল ভেরলেন চিহ্ণিত করেছিলেন অভিশপ্ত কবি হিসাবে । এই তালিকায় তিনি নিজেকেও অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন পুভ লেলিয়ান ( Pauvre Lélian ) ছদ্মনামে । উল্লেখ্য যে ১৮৮৪ সালে স্ত্রী মাতিলদে ভেরলেনকে আইনত ডিভোর্স করেছিলেন ।
পল ভেরলেন তাঁকে ‘অভিশপ্ত কবি’ সংকলনে অন্তর্ভুক্ত করার আগে ত্রিস্তঁ করবিয়ের ( ১৮৪৫ - ১৮৭৫ ) ফরাসি আলোচকদের কাছে সম্পূর্ণ অবহেলিত ছিলেন ; বহুকাল পরে এজরা পাউণ্ড ও টি. এস. এলিয়ট তাঁর কবিতা বিশ্লেষণের পর ত্রিস্তঁ করবিয়েরকে কাব্যসাহিত্যে গুরুত্ব দেয়া আরম্ভ হয় । করবিয়েরের মা, মারি-অঞ্জেলিক-আসপাসি পুয়ো’র বয়স যখন উনিশ তখন করবিয়েরের জন্ম হয় । তাঁর বাবা আঁতোয়াঁ-এদুয়া করবিয়ের ‘লে নেগরিয়ের’ নামে একটি উপন্যাস লিখেছিলেন । রাজকীয় উচ্চবিদ্যালয়ে ১৮৫৮ থেকে ১৮৬০ পর্যন্ত পড়ার সময়ে তিনি ডিপ্রেশনে আক্রান্ত হন এবং রিউমেটিজমের কারণে হাত-পা বিকৃত হয়ে যায় । বাড়ি থেকে অনেক দূরে স্কুলে দেবার এবং শারীরিক বিকৃতির দরুন তিনি বাবা-মাকে দোষ দিতেন । স্কুলের কড়া নিয়মনীতি ও শিক্ষদের প্রতি ঘৃণা তাঁর কবিতায় একটি বিশেষ কন্ঠস্বর গড়ে দিতে পেরেছে।করবিয়ের মারা যান যক্ষ্মারোগে, মাত্র তিরিশ বছর বয়সে । করবিয়েরের একটি কবিতা :
বিপরীত কবি
আরমোরিকার সাগরতীরে । একটি নির্জন মঠ ।
ভেতরে : বাতাস অভিযোগ করছিল : আরেকটা হাওয়াকল ।
এলাকার সমস্ত গাধা বীজসুদ্ধ আইভিলতায় তাদের দাঁত ঘষতে এসেছিল
ফুটোয় ভরা এমনই এক দেয়াল থেকে যা কোনও জীবন্ত মানুষ
দরোজার ভেতর দিয়ে ঢোকেনি।
একা— তবু নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে, ভরসাম্য বজায় রেখে,
একজন বুড়ির থুতনির মতন ঢেউখেলানো
তার ছাদ কানের পাশে চোট দিয়েছিল,
হাবাগবা মানুযের মতন হাঁ করে, মিনারটা দাঁড়িয়েছিল ।
অভিশপ্ত কবি জাঁ আর্তুর র্যাঁবোর ( ১৮৫৪ - ১৮৯১ ) কবিতার সঙ্গে পাঠকরা পরিচিত ; তাঁর ‘ইল্যুমিনেশানস’ বইটির নামকরণ করেছিলেন পল ভেরলেন । বইটি থেকে ‘শহর’ শিরোনামের গদ্যকবিতা :
এক মহানগর যাকে এই জন্যে আধুনিক মনে করা হয় যে বাড়িগুলোর বাইরের দিক সাজানোয় আর নগরের পরিকল্পনায় প্রয়োগ করার জন্য পরিচিত উপলব্ধিগুলো এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে ; তারই আমি এক ক্ষণজীবী আর তেমন বিচ্ছিন্ন নাগরিক নই । এখানে তুমি কুসংস্কারের একটিও স্মৃতিস্তম্ভের হদিশ পাবে না । সংক্ষেপে, নৈতিকতা আর ভাষাকে সরলতম প্রকাশে নামিয়ে আনা হয়েছে ! লক্ষাধিক এই লোকজন যারা পরস্পরকে জানার প্রয়োজন অনুভব করে না, নিজেদের শিক্ষাদীক্ষা, কর্মকাণ্ড, বার্ধক্যে এতো মিল যে তাদের আয়ু মহাদেশের গোলমেলে সংখ্যাতত্ব যা বলেছে তার চেয়েও বেশ কম । তাই, আমার জানালা দিয়ে, দেখতে পাই নতুন প্রেতরা শাশ্বত ঘন ধোঁয়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছে --- আমাদের বনানীঘেরা ছায়া, আমাদের গ্রীষ্মের রাত ! -- প্রতিহিংসর নতুন গ্রিক দেবতারা, আমার কুটিরের সামনে, যা আমার স্বদেশ, আমার সমগ্র হৃদয়, কেননা এখানে সবকিছুরই পরস্পরের সঙ্গে মিল আছে -- ক্রন্দনহীন মৃত্যু, আমাদের সক্রিয় কন্যা আর চাকরানি, রাস্তার কাদায় বেপরোয়া ভালোবাসা আর ফালতু অপরাধ ফুঁপিয়ে বেড়াচ্ছে ।
স্তেফান মালার্মে ( ১৮৪২ - ১৮৯৮ ) বাঙালি পাঠকের কাছে তিনি ‘এ রোল অব ডাইস উইল নেভার মিস এ চান্স’ কবিতাটির টাইপসেটিং সাজানোর ও সেকারণে মর্মার্থের বহুত্বের জন্য পরিচিত হলেও, বর্তমানে খুব বেশি পঠিত নন । বলা যায় যে ‘এ রোল অব ডাইস উইল নেভার মিস এ চান্স’ ইউরোপের কবিতার ধারায় বৈপ্লবিক ঘটনা ছিল; ঘুটির চাল ডিগবাজি খেতে-খেতে এঁকে বেঁকে যেভাবে এগিয়ে যেতে পারে সেইভাবে পঙক্তিগুলো সাজিয়েছিলেন মালার্মে ।কবিতার মধ্যে সহজাত শুদ্ধতা ও পরিপূর্ণতা আনার প্রচেষ্টায় ভাষাগত সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করতে না পেরে তিনি প্রায়ই উদ্ভাবনী শব্দ বিন্যাস, জটিল উপমা ও পরীক্ষামূলক মুদ্রণবিদ্যা প্রয়োগ করে কবিতা লিখে পাঠকের বিশ্লেষণ ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। মালার্মের সাহিত্য চর্চায় সারা জীবনের গোঁ ছিল যে, পাঠকরা প্রতীকের অর্থ বুঝুক । সাহিত্য ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক তুষ্টিকে তিনি অবজ্ঞার চোখে দেখতেন । তাঁর বাড়িতে প্রতি মঙ্গলবার সাহিত্যিকদের আড্ডা বসতো, কিন্তু স্কুলে শিক্ষকতা করার দরুণ তাঁর আর্থিক অবস্হা কোনো দিনই ভালো ছিল না ।স্বাভাবিক যে পাঠকদের মনে হয়েছে তাঁর কবিতার ভেতরে ঢোকা যায় না । এখানে তাঁর ‘কবিতার আবির্ভাব’-এর বাংলায়ন দিচ্ছি
দু:খি হয়ে পড়ছিল চাঁদ। কাঁদুনে দেবশিশুরা স্বপ্ন দেখছিল।
শান্ত ও বাষ্পীয় ফুলের তোড়ায় তাদের তীরবাহী আঙুল
যেন তাদের মরণাপন্ন বেহালার তার বাজছিল
আর আকাশ-নীল ফুলের পাপড়িতে গড়িয়ে পড়ছিল স্বচ্ছ অশ্রু।
সে ছিল তোমার প্রথম চুমুর আশীর্বাদ-পাওয়া দিন,
আর আমি আমার স্বপ্নের কাছে শহিদ হলুম,
যা বিষাদের সুগন্ধীর উপর ভর করে বেঁচেছিল,
এমনকি কোনও পরিতাপ বা দূর্ঘটনা ছাড়াই
একটি স্বপ্নকে সেই হৃদয়ের কাছে রেখে গিয়েছে
যে প্রথম স্বপ্নটি তুলেছিল।
এখানে আমি ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম, পাথরে বাঁধানো রাস্তায়
আমার চোখ নাচছিল।
যখন তুমি চুলে সূর্যের উচ্ছাস নিয়ে, রাস্তায় আর রাতের বেলায়
হাসিমুখে আমার কাছে এসেছো,
আর আমি ভাবলুম আলোর টুপি পরা এক পরীকে দেখছি,
যে আমার ছোটোবেলাকার ঘুমে স্বপ্নে দেখা দিত,
আর যার আধখোলা-মুঠো থেকে
সুগন্ধী নক্ষত্রের দলে ঝরে পড়তো তুষারপুঞ্জ
গাছেদের সরু ডালে ।
মহিলা কবি মার্সেলিন দেবোর্দে-ভামো’’র ( ১৭৮৬ - ১৮৪৯ ) জন্ম রনেঁর দুয়া তে। ফরাসি বিপ্লবের কারণে তাঁর বাবার ব্যবসা নষ্ট হয়ে যায় এবং আর্থিক সাহায্যের জন্য মায়ের সঙ্গে গুয়াদালুপ চলে যান; সেখানে তাঁর মা জনডিসে মারা যান আর ষোলো বছর বয়সী মারসেলিঁকে প্যারিসে ফিরে নাটকের দলে যোগ দিয়ে রোজগারের পথ বেছে নিতে হয় । ১৮১৭ সালে নাটকদলের একজন মামুলি অভিনেতা প্রসপার লাশান্তাঁ-ভামোকে বিয়ে করেন । ১৮১৯ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর কাব্যগ্রন্হ ‘এলেজি এবং রোমান্স’ । ১৮২১ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর ক্রীতদাসদের নিয়ে লেখা উপন্যাস ‘অ্যান্টিলেসের সন্ধ্যা’ । তাঁর ‘উদ্বেগ’ কবিতার বাংলায়ন দিচ্ছি এখানে ; ওনার নাম বাঙালি পাঠক শুনেছেন বলে মনে হয় না ; বাঙালি পাঠকের কাছে তিনি সত্যিই অভিশপ্ত :
কি যে আমাকে বিপর্যস্ত করে ? কেনই বা অপেক্ষা করব ?
এই শহরে, বড়ো বেশি বিষাদ ; তা থেকে, প্রচুর অবসর ।
আধুনিক সুখানুভব নামে যা চলছে
প্রতি ঘণ্টার পেষাই থেকে আমাকে সুরক্ষিত করতে পারে না ।
একসময়ে বন্ধুত্ব ছিল, কোনো বইয়ের আকর্ষণ
চেষ্টা ছাড়াই ভরে তুলতো অতিরিক্ত সময় ।
ওহ এই অস্পষ্ট আকাঙ্খার উদ্দেশ্য কি ?
আমি তা এড়িয়ে যাই, কিন্তু উদ্বেগ আমাকে ফিরে দেখতে বলে ।
আনন্দ যদি আমার হর্ষে ধরা না দ্যায়
তাহলে আমি তাকে দুঃখের বিশ্রামেও পাবো না,
তাহলে কোথায়ই বা পাওয়া যায় আমোদপ্রমোদ ?
আর তুমি যে আমাকে যা চাইছি তা দিতে পারো,
তুমি কি আমাকে চিরকালের জন্য ছেড়ে যাবার নির্ণয় নিয়েছ ?
আমাকে বলো, যুক্তিতর্ক, অনিশ্চিত, বিভ্রান্তিকর,
তুমি কি প্রেমের ক্ষমতাকে অনুমতি দেবে আমায় দখল করতে ?
হায়, নামটা শুনলেই আমার হৃদয় কেঁপে ওঠে !
কিন্তু যে ভয় উদ্বুদ্ধ করে তা অমায়িক আর সত্যি ।
যুক্তিতর্ক, তোমার কাছে ফাঁস করার মতন আর কোনো গোপনীয়তা নেই,
আর আমি ভাবি এই নামটি তোমার চেয়ে তাদের কথা বেশি বলেছে !
এবার জানা যাক আগুস্তে ভিলিয়ার্স দ্যলিজলে আদঁ-র ( ১৮৩৮ -৮৯ ) কথা । ব্রিট্যানির এক অভিজাত পরিবারে জন্ম, যদিও তাঁদের আর্থিক অবস্হা ভালো ছিল না আর নির্ভর করতে হতো মায়ের কাকিমা মাদামোয়াজেল দ্য কেরিনুর দান-খয়রাতের ওপর । তার ওপর ভিলিয়ার্সের বাবার গোঁ চাপে যে তিনি মালটায় গিয়ে ফরাসি বিপ্লবের সময়ে লুকোনো গুপ্তধন উদ্ধার করবেন । ফলে তিনি জমি কিনতেন আর গুপ্তধন না পেয়ে বেচতেন । এই করে ফতুর হয়ে যান । ভিলিয়ার্সকেও ডজনখানেক স্কুল পালটাতে হয় । ১৮৫০ এর পর তিনি বেশ কয়েকবার প্যারিসে গিয়ে কাজের খোঁজ করে কিছুই যোগাড় করতে পারেননি । পাকাপাকি প্যারিসে থাকার ব্যবস্হার জন্য তাঁর এক আত্মীয়া মাসিক খরচের ব্যবস্হা করেন । তিনি ল্যাটিন কোয়ার্টারের মদ্যপ কবি-লেখকদের আড্ডায় যোগ দ্যান এবং শার্ল বোদলেয়ারের পরামর্শে এডগার অ্যালান পোর রচনাবলী পড়া আরম্ভ করেন । ১৮৫৯ সালে নিজের টাকায় প্রকাশ করেন ‘প্রথম কবিতাবলী’ । বইটা কোথাও আলোচিত হলো না । উপরন্তু তিনি লুইজি দায়োনে নামে এক বহুবল্লভা যুবতীর সঙ্গে বসবাস আরম্ভ করলেন ; তাঁর পরিবারে সদস্যদের চাপে ১৮৬৪ সালে যুবতীটিকে ছেড়ে গীর্জায় আশ্রয় নিতে হয় । ভিলিয়ার্স অনেক চেষ্টা করেও বিয়ে করার মতন যুবতী পাচ্ছিলেন না ; তিনি থিয়োফিল গতিয়েকে তাঁর মেয়ে এসতেলে সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব দিলে গতিয়ের তাঁকে তাড়িয়ে দিয়ে বলেন যে তিনি ভবঘুরে মাতাল অখ্যাত কবির সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে চান না । অ্যানা আয়ার পাওয়েল নামে বৈভবশালী ইংরাজ যুবতীকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েও প্রত্যাখ্যাত হন । শেষে তিনি এক বেলজিয় ঘোড়ার গাড়ির চালকের অশিক্ষিতা বিধবা স্ত্রী মারি দানতিনের সঙ্গে বসবাস আরম্ভ করেন আর ১৮৮১ সালে তাঁর ছেলে ভিক্তরের জন্ম হয় । কিন্তু কবিস্বীকৃতি, ভেরলেনের বইতে অন্তর্ভুক্ত হবার আগে, তিনি পাননি । এখানে ভিলিয়ার্সের ‘স্বীকৃতি’ কবিতাটির বাংলায়ন :
যবে থেকে আমি শব্দগুলো ভুলে গেছি, যৌবনের
ফুল আর এপ্রিলের টাটকা বাতাস…
আমাকে তোমার ঠোঁট দুটি দাও ; তাদের সুগন্ধি যৌতুক
গাছেদের ফিসফিস কথাবার্তা হয়ে দেখা দেবে !
যবে থেকে আমি গভীর সমুদ্রের দুঃখ হারিয়েছি
মেয়েটির কান্না, তার অস্হির টান, তার মৃত্যুর আলয়…
একটা শব্দেরও শ্বাস ফেলে না ; তা বিষাদ বা আনন্দ
হয়ে উঠবে ঢেউদের কলকল-ধ্বনি !
যবে থেকে আমার আত্মায় অন্ধকারের ফুল
আত্মমগ্ন, আর পুরোনো সূর্ষেরা উড়াল নেয়…
প্রিয়তমা আমাকে তোমার মলিন বুকে লুকিয়ে নাও,
আর তা হয়ে উঠবে রাতের প্রশান্তি !
কিন্তু অভিশপ্ত কবিদের তালিকায় তাঁর গুরু শার্ল বোদলেয়ার, কোঁতেদ্য লুতিয়ামোঁ (Comte de Lautréamont ) , অ্যালিস দ্য শমবিয়ে ( Alice de Chambrier ), আঁতোনা আতো ( Antonin Artaud ), জঁ-ফিয়ে দ্যুফে ( Jean-Pierre Duprey ) প্রমুখকে যোগ করেন পরবর্তীকালের আলোচকরা ; বস্তুত পল ভেরলেনই ছিলেন সবচেয়ে বেশি অভিশপ্ত। এই কবিরা তাঁদের কবিতার জন্য অভিশপ্ত নন ; তাঁদের জীবনের দুঃখ, বিষাদ, আর্থিক দৈন্য, পরাজয়বোধ, অবহেলা, মাদকে আসক্তি, যৌনরোগ ইত্যাদির কারণে তাঁদের মনে করা হয়েছে ‘অভিশপ্ত’। তাঁর মৃত্যুর পর Fin de siècle বা শতাব্দী শেষের কবিদের অন্যতম মনে করে হয় পল ভেরলেনকে।
প্রথমে পড়া যাক শার্ল বোদলেয়ারের গদ্য কবিতার বই ‘বিষণ্ণ প্যারিস’ এর একটি রচনা :
আমাকে তোমার চুলের দীর্ঘ, দীর্ঘ সুগন্ধ নিতে দাও, ঝর্ণার জলে পিপাসার্তের মতন আমার মুখকে সম্পূর্ণ ডুবে জেতে দাও, সুবাসিত রুমালের মতন হাতে নিয়ে খেলতে দাও, বাতাসে স্মৃতিকে উড়িয়ে দিতে দাও ।
আমি যাকিছু দেখি তা তুমি যদি জানতে -- যাকিছু আমি অনুভব করি -- তোমার চুলে যাকিছু আমি শুনতে পাই ! অন্য লোকেদের আত্মা সঙ্গীতের প্রভাবে যেমন ভ্রমণে বেরোয় তেমনই আমার আত্মা ভ্রমণে বেরোয় এই সুগন্ধে।তোমার চুলে রয়েছে একটি পুরো স্বপ্ন, পাল আর মাস্তুলসহ ; তাতে রয়েছে বিশাল সমুদ্র, যেখানে অগুনতি মৌসুমীবায়ু আমাকে বয়ে নিয়ে যায় মোহিনী আবহাওয়ায়, যেখানে আকাশ আরও নীল আর আরও নিগূঢ়, যেখানে বাতাবরণকে সুগন্ধিত করে তুলেছে ফল, পাতা, আর মানুষের ত্বক।
তোমার চুলের সাগরে, আমি দেখতে পাই দুঃখী গানে সমাহিত বন্দর, সব কয়টি দেশের কর্মঠ মানুষ সেখানে, যতো রকম হতে পারে ততো ধরণের জাহাজ, বিশাল আকাশের অলস শাশ্বত তাপের পৃষ্ঠভূমিতে তাদের স্হাপত্য দিয়ে দিগন্তকে তনূকৃত ও জটিল করে তুলেছে।
তোমার চুলের সোহাগস্পর্শে আমি কাউচে শুয়ে কাটানো দীর্ঘ ধীরুজ সময়কে ফিরে পাই, সুন্দর জাহাজের একটি ঘরে, বন্দরের অনির্ণেয় ঢেউয়ের দ্বারা ক্রমান্বয়ে দোল খাওয়া, তাজা জলের জালা আর ফুলের টবের মাঝে ।
আগুনের পাশে রাখা কম্বলের মতন তোমার চুলে, আমি আফিম আর চিনির সঙ্গে মেশানো তামাকের শ্বাস নিই ; তোমার চুলের রাত্রিতে, আমি দেখতে পাই অসীম ক্রান্তিবৃত্তের নীলাভ ঔজ্বল্য; তোমার চুলের ঢালের কিনারায়, আমি আলকাৎরা, মৃগনাভি আর নারিকেল তেলের গন্ধে মাতাল হয়ে যেতে থেকি ।
আমাকে একটু-একটু করে খেয়ে ফেলতে থাকে তোমার তন্দ্রাতুর কালো বিনুনি । যখন তোমার স্হিতিস্হাপক, দ্রোহী চুল আমি চিবোতে থাকি, আমার মনে হয় আমি স্মৃতিগুলো খেয়ে ফেলছি।
কঁতে দ্য লুতিয়ামোর ( ১৮৪৬ - ১৮৭০ ) প্রকৃত নাম ইসিদোরে লুসিয়েন দুকাস, জন্মেছিলেন উরুগুয়েতে । তাঁর জন্মের পরেই মা মারা যান ; তখন আর্জেনটিনা আর উরুগুয়ের যুদ্ধ চলছে । তাঁর বাবা, যিনি ফরাসিভাষী ছিলেন, তাঁকে তেরো বছর বয়সে প্যারিসে পাঠিয়ে দ্যান স্কুল শিক্ষার জন্য । সতেরো বছর বয়সে উচ্চ বিদ্যালয়ে তিনি দাঁতে, মিলটন, বোদলেয়ার এবং রাসিনে মুখস্হ বলতে পারতেন বলে শিক্ষকদের প্রিয় ছিলেন । কিন্তু নির্ণয় নেন যে তিনি নিজে ‘নিষ্ঠুরতার আনন্দবোধ’ নিয়ে কবিতা লিখবেন । ‘মালদোরোরের গান’ নামে তিনি একটি কাব্যোপন্যাস লেখেন, ১৯৬৮ থেকে ১৯৬৯ সালের মাঝে, তাঁর এই নির্ণয়কে রূপ দেবার জন্য । নায়কের নাম মালদোরোর । বইটি ছয় পর্বে আর ষাটটি কবিতাংশে বিভাজিত । ডাডাবাদীরা, পরাবাস্তববাদীরা, বিশেষ করে সালভাদোর দালি, তাঁর এই বইটির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন । বইটির বহু দৃশ্যের এচিং করেছিলেন দালি । আমি বইটি থেকে একটি কবিতাংশ তুলে দিচ্ছি:
আমি নোংরা । আমার সারা শরীরে উকুন । শুয়োররা, যখন আমার দিকে তাকায়, বমি করে। আমার চামড়া কুষ্ঠরোগের মামড়ি আর আঁশে ছয়লাপ, আর তার ওপরে হলুদ রঙের পুঁজ । আমার বাঁদিকের বগলে এক ব্যাঙ পরিবার বসবাস আরম্ভ করেছে, আর, তাদের কোনো একটা নড়াচড়া করলে, কাতুকুতু দ্যায় । মনে রাখতে হয় যাতে বাইরে বেরিয়ে মুখ দিয়ে কান আঁচড়াতে না আরম্ভ করে ; তাহলে সেটা মগজে ঢুকে যাবে । আমার ডানদিকের বগলে রয়েছে একটা গিরগিটি যে সব সময়ে ওদের তাড়া করে যাতে খাবার না জোটায় মারা যায় : সবাইকে তো বাঁচতে হবে । আমার পোঁদের ভেতরে একটা কাঁকড়া ঢুকে গেছে ; আমার কুঁড়েমিতে উৎসাহিত হয়ে, ঢোকার পথটা নিজের দাড়া দিয়ে পাহারা দ্যায় আর আমাকে দ্যায় অসহ্য যন্ত্রণা ।
অ্যালিস দ্য শমবিয়ে ( ১৮৬১ - ১৮৮২ ) একুশ বছর বয়সে কোমায় আক্রান্ত হয়ে মারা যান, তার কিছুকাল আগেই তিনি লিখেছিলেন ‘ঘুমন্ত সুন্দরী’ । তাঁর অধিকাংশ বই প্রকাশিত হয়েছে তাঁর মৃত্যুর পর । এখানে তাঁর ‘পলাতক’ কবিতাটির বাংলায়ন :
আমরা সবাই আগন্তুক আর পৃথিবী হয়ে চলে যাই
খেলার সময়ে উধাও আলোর নৌকোর মতো
হালকা হাওয়ায় চুপিচুপি চুমুর আড়ালে,
আর নীল দিগন্ত ক্রমশ বিলীন হয়ে যায় ;
উড়ালের সময়ে যদি হলরেখার খাত গড়তে পারে তাহলে আনন্দিত
সে চলে যাবার পরে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করো ;
যে পথ সে দ্রুত যাত্রায় খুঁজতে চেয়েছিল
কোনো ঘুর্ণিঝড় তাকে মুছে দিতে পারে না;
আনন্দিত, যদি অদৃষ্ট আমাদের টেনে বের করে আনে
আমরা তবুও হৃদয় হয়ে বাঁচি যেখানে থেকেছি চিরকাল,
সুদূর সমুদ্রতীর পর্যন্ত যে হৃদয় আমাদের অনুসরণ করে
তাহলে এখানে এক মৃত মানুষের সমাধিকে কী বলা হবে ?
আঁতোনা জোসেফ মারি আতো ( ১৮৯৬ - ১৯৪৮ ), যিনি আঁতোনা আতো নামে অধিক পরিচিত, ছিলেন কবি, নাট্যকার, প্রাবন্ধিক, অভিনেতা, নাট্য পরিচালক এবং ইউরোপীয় আভাঁগার্দ আন্দোলনের পুরুষদের অন্যতম । ‘থিয়েটার অব ক্রুয়েলটি’ তত্বটির জন্য তিনি অধিকতর পরিচিত । যদিও তাঁর জন্ম ফ্রান্সের মার্সাইতে, তাঁর বাবা-মা ছিলেন গ্রিক । জাহাজের মালিক ছিলেন তাঁর বাবা । তাঁর মায়ের নয়টি বাচ্চা হয়েছিল, চারটি মৃত অবস্হায় জন্মায় আর দুটি শৈশবেই মারা যায় । পাঁচ বছর বয়সে আতো আক্রান্ত হন মেনেনজাইটিসে, যার দরুন কোমাটোজে ছিলেন কিছুকাল এবং বিভিন্ন স্যানাটোরিয়ামে চিকিৎসার জন্য পাঁচ বছর ভর্তি ছিলেন । ১৯১৬ সালে তাঁকে বাধ্যতামূলক সেনাবাহিনিতে যোগ দিতে হয়েছিল কিন্তু মানসিক অস্হিরতার কারণে ছাঁটাই হন । দীর্ঘ রোগভোগের দরুণ তাঁকে ল্যডানডাম ওষুধ ( অ্যালকোহলে গোলা আফিম ) নিতে হতো আর সেখান থেকেই তাঁর আফিমের নেশা ।সাতাশ বছর বয়সে তিনি এক গোছা কবিতা ‘নতুন ফরাসি রিভিউ’ ( Nouvelle Revue Française ) পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠান ; তা প্রত্যাখ্যাত হলেও সম্পাদক তাঁর কবিতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে চিঠি লেখেন এবং বেশ কিছু সময় তাঁদের মধ্যে চিঠির আদান-প্রদান হয় । এখানে তাঁর কয়েকটা কবিতার বাংলায়ন দিলুম, কেননা তাঁর কবিতার বই সহজে পাওয়া যায় না :
নিরংশু কবি
নিরংশু কবি, একটি তরুণীর বুক
তোমাকে হানা দিয়ে বেড়ায়,
তিক্ত কবি, জীবন ফেনিয়ে ওঠে
আর জীবন পুড়তে থাকে,
আর আকাশ নিজেকে বৃষ্টিতে শুষে নেয়,
জীবনের হৃদয়ে নখের আঁচড় কাটে তোমার কলম ।
অরণ্য, বনানী, তোমার চোখ দিয়ে প্রাণবন্ত
অজস্র ছেঁড়া পালকের ওপরে ;
ঝড় দিয়ে বাঁধা চুলে কবি চাপেন ঘোড়ায়, কুকুরের ওপরে ।
চোখ থেকে ধোঁয়া বেরোয়, জিভ নড়তে থাকে
আমাদের সংবেদনে স্বর্গ উথালপাথাল ঘটায়
মায়ের নীল দুধের মতন ;
নারীরা, ভিনিগারের কর্কশ হৃদয়,
তোমাদের মুখগহ্বর থেকে আমি ঝুলে থাকি ।
আমার টাকাকড়ি নেই
আমার টাকাকড়ি নেই কিন্তু
আমি
আঁতোনা আতো
আর আমি ধনী হতে পারি
ব্যাপকভাবে আর এক্ষুনি ধনী হতে পারি
যদি আমি তার জন্য প্রয়াস করতুম ।
সমস্যা হলো আমি চিরকাল টাকাকড়িকে,
ধনদৌলতকে, বৈভবকে ঘৃণা করেছি ।
কালো বাগান
এই কালো পাপড়িগুলো ভারতের আকাশের ঘুর্ণাবর্তকে ঘোরাও।
ছায়ারা পৃথিবীকে ঢেকে ফেলেছে যা আমাদের সহ্য করে ।
তোমার নক্ষত্রদের মাঝে চাষের জমিতে পথ খুলে দাও ।
আমাদের আলোকিত করো, নিয়ে চলো তোমার নিমন্ত্রণকর্তার কাছে,
চাঁদির সৈন্যবাহিনী, নশ্বর গতিপথে
আমরা রাতের কেন্দ্রের দিকে যেতে চেষ্টা করি ।
আমি কে
আমি কে ?
আমি কোথা থেকে এসেছি ?
আমি আঁতোনা আতো
আর আমি একথা বলছি
কেননা আমি জানি তা কেমন করে বলতে হয়
তাৎক্ষণিকভাবে
তুমি আমার বর্তমান শরীরকে দেখবে
ফেটে গিয়ে বহু টুকরো হয়ে গেছে
আর তাকে আবার গড়ে ফেলবে
দশ হাজার কুখ্যাত পরিপ্রেক্ষিতে
এক নতুন শরীর
তখন তুমি আমাকে
কখনও ভুলতে পারবে না ।
স্নায়ু ছন্দ
একজন অভিনেতাকে দেখা হয় যেন স্ফটিকের ভেতর দিয়ে ।
মঞ্চের ওপরে অনুপ্রেরণা ।
সাহিত্যকে বেশি প্রবেশ করতে দেয়া উচিত নয় ।
আমি আত্মার ঘড়ি ধরে কাজ করা ছাড়া আর কোনো চেষ্টা করিনি,
আমি কেবল নিষ্ফল সমন্বয়ের যন্ত্রণাকে লিপ্যন্তর করেছি ।
আমি একজন সম্পূর্ণ রসাতল ।
যারা ভেবেছিল আমি সমগ্র যন্ত্রণার যোগ্য, এক সুন্দর যন্ত্রণা,
এক ঘন আর মাংসল পীড়া, এমন এক পীড়া যা বিভিন্ন বস্তুর মিশ্রণ,
বুদবুদ-ভরা একটি নিষ্পেশিত ক্ষমতা
ঝুলিয়ে রাখা বিন্দু নয় — আর তবু অস্হির, উপড়ে-তোলা স্পন্দনের সাহায্যে
যা আমার ক্ষমতা আর রসাতলের দ্বন্দ্ব থেকে আসে
শেষতমের উৎসার দেয় ( ক্ষমতার তেজের দ্বন্দ্বের মাপ বেশি ),
আর কোনও কিছু বাকি থাকে না বিশাল রসাতলগুলো ছাড়া,
স্হবিরতা, শীতলতা–
সংক্ষেপে, যারা আমাকে অত্যধিক জীবনের অধিকারী মনে করেছিল
আত্মপতনের আগে আমার সম্পর্কে ভেবেছিল,
যারা মনে করেছিল আমি যন্ত্রণাদায়ক আওয়াজের হাতে নির্যাতিত,
আমি এক হিংস্র অন্ধকারে লড়াই করেছি
তারা সবাই মানুষের ছায়ায় হারিয়ে গেছে ।
ঘুমের ঘোরে, আমার পুরো পায়ে স্নায়ুগুলো প্রসারিত হয়েছে ।
ঘুম এসেছে বিশ্বাসের বদল থেকে, চাপ কমেছে,
অসম্ভাব্যতা আমার পায়ের আঙুলে জুতো-পরা পা ফেলেছে ।
মনে রাখা দরকার যে সমগ্র বুদ্ধিমত্তা কেবল এক বিশাল অনিশ্চিত ঘটনা,
আর যে কেউ তা খুইয়ে ফেলতে পারে, পাগল বা মৃতের মতন নয়,
বরং জীবিত মানুষের মতন, যে বেঁচে আছে
আর যে অনুভব করে জীবনের আকর্ষণ আর তার অনুপ্রেরণা
তার ওপর কাজ করে চলেছে ।
বুদ্ধিমত্তার সুড়সুড়ি আর এই প্রতিযোগী পক্ষের আকস্মিক প্রতিবর্তন ।
বুদ্ধিমত্তার মাঝপথে শব্দেরা ।
চিন্তার প্রতিবর্তন প্রক্রিয়ার সম্ভাবনা একজনের চিন্তাকে হঠাৎ নোংরামিতে পালটে দ্যায় ।
এই সংলাপটি চিন্তার অন্তর্গত ।
ভেতরে ঢুকিয়ে নেয়া, সবকিছু ভেঙে ফেলা ।
আর হঠাৎ আগ্নেয়গিরিতে এই পাতলা জলের স্রোত, মনের সরু, আস্তে-আস্তে পতন ।
আরেকবার নিজেকে ভয়ঙ্কর অভিঘাতের মুখোমুখি আবিষ্কার করা, অবাস্তবের দ্বারা নিরসিত, নিজের একটা কোনে, বাস্তব জগতের কয়েকটা টুকরো-টাকরা ।
আমিই একমাত্র মানুষ যে এর পরিমাপ করতে পারি ।
১৯৫০ সালে, কুড়ি বছর বয়সে, জাঁ ফিয়ে দুফের (১৯৩০ - ১৯৫৯ ) প্রথম কবিতার বই ‘দ্বিতীয়ের পেছনে’র পাণ্ডুলিপি পড়ে আঁদ্রে ব্রেতঁ তাঁর প্রশংসা করেছিলেন । এক বছর পরে তিনি কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়ে ভাস্কর্যে আগ্রহী হন, আর পাঁচের দশকের পুরো সময় লোহা আর সিমেন্টের কাজ করেন, সেই সঙ্গে চারকোল ও কালির কাজও করেন । ১৯৫৯ সালে ব্যক্তিগত দ্রোহ প্রকাশ করার জন্য আর্ক দ্য ত্রয়েম্ফে অজানা সেনাদের শিখায় পেচ্ছাপ করার সময়ে ধরা পড়েন আর জনগণের পিটুনি খেয়ে প্রথমে কারাগারে আর তারপর পাগলাগারদে যেতে হয় । ছাড়া পেয়ে আবার কবিতা লেখা আরম্ভ করেন এবং ‘শেষ ও উপায়’ কাব্যগ্রন্হের পাণ্ডুলিপি স্ত্রীর হাতে দিয়ে নির্দেশ দ্যান তা ব্রেতঁকে ডাকে পাঠিয়ে দিতে । বাড়ি ফিরে স্ত্রী জ্যাকলাঁ দেখতে পান যে ছবি আঁকার ঘরের কড়িকাঠ থেকে ঝুলে জাঁ ফিয়ে দুফে আত্মহত্যা করেছেন । কাব্যগ্রন্হটি থেকে ‘সম্পূর্ণ’ শিরোনামের গদ্য কবিতাটির বাংলায়ন :
জগতসংসার সম্পূর্ণ । কে সেই লোক যে রাতকে প্রতিবার একই ফাঁদে ফ্যালে ? আমি, যদি বলা হয়, কাউকেই চিনি না আর যে আকাশ আমার ওপর মনের ঝাল মেটায়, ওর বড়ো ইঁদুরের হাত আমাকে কখনও, কখনও দেখায়নি ।
কেউ একজন দরোজাটা খুললো : ভেতরে ছিল না কেউ, ভেতরে তার ছিল হাড় আর হাড়, আর আমি প্রতিজ্ঞা করে সবাইকে জানিয়েছি যে আমি জ্যান্ত ওর চামড়া ছাড়িয়ে নেবো ।
জগতসংসার ভয়ঙ্করভাবে সম্পূর্ণ ছিল আর জিনিসপত্রের টানাটানি চলছিল । কেউ একজন দুঃস্বপ্নকে সাজিয়ে রাক্ষসদের আলোকিত করছিল আর তাকে বলা হচ্ছিল বর্তমান, এখন…
এই বর্তমানগুলো আমাদের বহু সংগ্রহকে সমৃদ্ধ করেছিল, আমি থেকে আমিতে, আমার থেকে আমার সঙ্গে আর অন্য অনেকের সঙ্গে, আর আমার সঙ্গে অন্য অনেকের...কিন্তু অনেকসময়ে সবচেয়ে বিচক্ষণ ভাগাভাগিও আমাদের আলাদা করতে পারে, কিন্তু মাথা কখনও, আর আমি বলতে চাই কখনও, কাঁধের ওপরে স্হিতিশীল থাকেনি ।
দুই
‘অভিশপ্ত বুদ্ধিজীবীদের’ কালখণ্ডে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন জাগে যে পল ভেরলেন চল্লিশ বছর বয়সে কয়েকজন কবিকে ‘অভিশপ্ত কবি’ চিহ্ণিত করে একটা বই লিখলেন কেন ? তিনি কি আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিলেন, নাকি নিজেকে দেখতে চাইছিলেন সেই কবিদের সারিতে যাঁদের তিনি গুরুত্বপূর্ণ কবি মনে করলেও তখনকার ‘বুর্জোয়া পাঠক’ কোনও পাত্তা দিতেন না । চল্লিশ বছর বয়সে র্যাঁবোকে খুনের চেষ্টার দায়ে জেল খেটে ফিরেছেন, একজনকে ( অনেকের মতে নিজের মা-কে ) মারধর করার কারণে আবার জেলে গিয়েছিলেন, রোমান ক্যাথলিক হিসাবে দীক্ষা নিয়েছেন, তবু তাঁর কেন মনে হয়েছিল তাঁর মতনই কয়েকজন কবি অভিশপ্ত ? সাধারণ পাঠকের কাছে তাঁরা ছিলেন অখ্যাত, সমাজ তাঁদের প্রতি উদাসীন ছিল কেননা তাঁদের কবিতা তারা বুঝে উঠতে পারছিল না । কেবল রসপণ্ডিতরা তাঁদের কবিতায় আগ্রহী ছিলেন আর সেকারণে তাঁদের জীবন দুর্দশাপূর্ণ ছিল । উপেক্ষার, এমনকি ‘বুর্জোয়া অশিক্ষিতদের দ্বারা’ পদদলিত হবার চর্চিত বোধ, হয়তো ছিল প্রথম পর্বের আভাঁ গার্দ লেখক-কবিদের ধ্রুপদি দাবি।ফরাসিদেশের কবি-চিত্রকরদের মাঝে আত্মক্ষয়ের গৌরব প্রশংসনীয় ছিল তাঁদের নিজেদের গণ্ডিতে ।
অভিশাপটি একই সঙ্গে যতোটা নৈতিক ও আত্মিক মনে করেছিলেন ভেরলেন, ততোটাই সামাজিক, যে মানসিকতা থেকে এই বোধের সূত্রপাত যে ‘সত্যকার শিল্পীকে’ প্রতিভার চাপ সহ্য করে ক্লেশ ও নিদারুণ-যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় । চল্লিশ বছর বয়সে ভেরলেন মাতলামি, স্ত্রী ও মাকে মারধর করে, বাচ্চাকে যাতনা দিয়ে, সিফিলিসে ভুগে, বস্তিতে জীবন কাটিয়ে, ভিক্ষাবৃত্তি করে, জীবনের মর্মভেদী যন্ত্রণাদায়ক অভিজ্ঞতাগুলোর সঙ্গে অতিপরিচিত হয়ে গিয়েছিলেন এবং কবিদের ক্ষেত্রে ‘অভিশাপ’ যে কেবল সমাজের দেয়া নয়, তাঁরা নিজেরাও এমন সমস্ত কাজকর্ম করেছেন যে প্রকৃতি তাঁদের জীবনে বিপদ ডেকে এনেছে, তাঁদের দেহ ও অন্তরজগতকে ক্ষইয়ে দিয়েছে, তা টের পেয়েছিলেন তিনি ।
পল ভেরলেনের কাছে ‘অভিশপ্ত কবির’ প্রধান দৃষ্টান্ত ছিলেন শার্ল বোদলেয়ার ( ১৮২১ - ১৮৬৭ ) যাঁর ‘পাপের ফুল’ ( Les fleurs du mal ), ১৮৫৭ সালে প্রকাশিত, ছিল উনিশ শতকের সবচেয়ে বিখ্যাত কাব্যগ্রন্হ এবং পৃথিবীর সাহিত্যে অতুলনীয় । বইটির কবিতাগুলোয় ছিল সৌন্দর্যের সঙ্গে ইতরতার বৈপ্লবিক মিশ্রণ, তাতে প্রতিফলিত হয়েছিল চরম আধ্যাত্মিকতা যার জন্য আধুনিক যুগ বহুকাল অপেক্ষা করছিল, যা একই সঙ্গে ছিল স্বর্গে ঝড়-তোলা ও নাছোড়বান্দাভাবে নারকীয় । মর্ত্যে নরকভোগের অভিজ্ঞতা শার্ল বোদলেয়ারের ছিল, এবং তার অধিকাংশ তাঁর নিজের গড়া নরক । লাতিন কোয়ার্টার থেকে তুলে এনেছিলেন এক শ্যামলী বেশ্যাকে, আর তার থেকে প্রেমের পাশাপাশি পেয়েছিলেন সিফিলিস । তেত্রিশ বছর বয়সে মাকে বোদলেয়ার লিখেছিলেন, “আমি প্রথম থেকেই জঘন্য।” অথচ উত্তরাধিকারসূত্রে যা টাকাকড়ি পেয়েছিলেন, তিনি সারাজীবন আরামে জীবন কাটাতে পারতেন । আঁতোনা আতোর মতন বোদলেয়ারও লডানডাম ( মদে মেশানো আফিম ) মাদকের নেশা ছাড়তে পারেননি । যে লোক নিজেকে অভিশপ্ত মনে করে, সে তার কারণ খোঁজে । বোদলেয়ারে পাওয়া যায় যিশুখ্রিস্টের উপহাস । ‘সেইন্ট পিটারের অস্বীকৃতি’ কবিতায় বোদলেয়ার বলছেন:
আহ ! যিশু, অলিভের বাগানকে মনে করো !
তোমার সারল্যে তুমি হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা করেছিলে তার কাছে
যে স্বর্গে রয়েছে সে হাসছিল পেরেকের শব্দে
যেগুলো নীচ জল্লাদেরা তোমার মাংসে পুঁতে দিচ্ছিল ।
বিশোধক যন্ত্রণাবোধের ধারণাকে বোদলেয়ার দিয়েছেন এক বিশেষ উতরাই, যা টেনেছিল পল ভেরলেনকে । ভেরলেন জানতেন যে বোদলেয়ারের নায়ক ছিলেন এডগার অ্যালান পো, যিনি, বোদলেয়ারের মতে, অত্যধিক মদ খাবার কারণে মারা যান, ‘অভিশপ্ত কবি’র সৃষ্টিক্ষমতা ও আত্মধ্বংসের ক্ষমতা দুটিই ছিল অ্যালান পোর অহংকার । বোদলেয়ারের চরস আর আফিমের নেশা ছিল যা তিনি ক্ষতিকর মনে করেও ছাড়তে পারেননি ; ‘অভিশপ্ত কবির’ যদি মনে হয় মাদক তাঁর চেতনাকে উন্নীত করছে, তাহলে তার ক্ষতিকর প্রভাবকে প্রতিভার দাম চোকানো হিসেবে তিনি মান্যতা দেবেন । এডগার অ্যালান পো, শার্ল বোদলেয়ার ও পল ভেরলেনের মাতাল-অবস্হায়-থাকা হয়ে উঠেছিল এক ধরণের আধ্যাত্মিক নিয়মনিষ্ঠা ।
পল ভেরলেন মধ্যস্হ, মীমাংসক, শান্তিস্হাপকের বেদিতে বসিয়েছিলেন শার্ল বোদলেয়ারকে । ভেরলেন লিখেছেন, “আমার কাব্যিক অনুভূতিকে, এবং আমার গভীরে যা রয়েছে, তাকে জাগিয়ে তুলেছিলেন বোদলেয়র।” একুশ বছর বয়সে ভেরলেন লিখেছিলেন, “শার্ল বোদলেয়ার উপস্হিত করতে পেরেছেন সংবেদনশীল মানুষকে, এবং তিনি তাকে উপস্হাপন করেন একটি আদর্শ হিসাবে, বা বলা যায়, নায়ক হিসাবে ।” ভেরলেন আরও বললেন যে, শার্ল বোদলেয়ার “একজন দ্রষ্টা ; তাঁর রয়েছে তীক্ষ্ণ, স্পন্দমান সংবেদন, একটি যন্ত্রণাময় নিগূঢ় মন, তাঁর ধীশক্তি তামাকে প্লাবিত, তাঁর রক্ত বিশুদ্ধ সুরাসারে প্রজ্বলন্ত ।” যেহেতু অভিশপ্ত, তাই আশীর্বাদপূত ।
বোদলেয়ারকে নায়কের বেদিতে বসিয়ে তাঁর জীবনযাত্রা অনুকরণের প্রয়াস করলেন পল ভেরলেন । মদে চোবানো অফিমের বদলে তিনি আসক্ত হলেন আবসাঁথে । আবসাঁথে আর কিছু মেশাতে হয় না, সরাসরি পান করতে হয় এবং গাঢ় নেশা হয় । বন্ধুরা নিষেধ করলে ভেরলেন তাঁদের সঙ্গে তরোয়াল বের করে মুখোমুখি হতেন । ভেরলেনের হাতে দেশলাই দেখলে তাঁর বন্ধুরা ভয় পেতেন । স্ত্রীর চুল সুন্দর বলে তাতে আগুন ধরাবার চেষ্টা করেছিলেন । যখন ‘অভিশপ্ত কবি’ ভেরলেন লিখছেন, এবং দুঃখদুর্দশায় জীবন কাটাচ্ছেন, তিনি জানতেন না যে তাঁর বেশ কিছু কবিতা সাধারণ পাঠকের কাছে পৌঁছেচে । কিন্তু তাঁর মনের মধ্যে ক্ষোভ মৃত্যু পর্যন্ত ছিল যে তাঁকে আর তাঁর কবিতাকে কেউ ঠিকমতন বুঝতে পারেনি ; তাঁর মনে হতো একজন কবির কাব্যিক প্রতিভার কারণে যে আবেগের ঝড় তাকে পুষতে হয় তা লোকে টের পায় না ; প্রথানুসরণ সত্যকার শিল্পের শ্বাসরোধ করে, তাই সীমালঙ্ঘন জরুরি হয়ে ওঠে মৌলিকতাকে আয়ত্ব করার জন্য, নয়তো কবিতা হয়ে উঠবে আহরিত ; জীবনকে আত্মাহীন হলে চলবে না, তাকে হতে হবে অকৃত্রিম ও বিশ্বাসযোগ্য ।
বোদলেয়ার, ভেরলেন, র্যাঁবোর সময়ে, ইউরোপেও, অভিশপ্ত কবির যুক্তি খাটতো, কিন্তু এখন সেগুলো কিংবদন্তি মনে হয় । ইউরোপ-আমেরিকায় নৈতিক বিপথগামীতার নতুন সংজ্ঞা বাজারের চালচলনের সঙ্গে বদলাতে থাকে । এমনকি ভারতেও বোদলেয়ার বা ভেরলেনের মতন অভিশপ্ত কবির যুগ শামসের আনোয়ার ও ফালগুনী রায়ের সঙ্গে শেষ হয়ে গেছে । এখন এসেছে অভিশপ্ত বুদ্ধিজীবির কালখণ্ডে । যাতে উপেক্ষার অভিশাপে না পড়তে হয় তাই কবি-লেখকরা এখন শাসকদলের ছত্রছায়ায় আশ্রয় নিতে চান । পশ্চিমবঙ্গে সিপিএমের সময়ে যাঁরা লাল ঝাণ্ডা নিয়ে মিছিল করতেন তাঁরা অনেকেই তৃণমূলের মন্ত্রীর পাশে বসে ফোটো তোলাতে কার্পণ্য করেন না। রাষ্ট্র এখন এমনই বেপরোয়া যে কাকে কোন অভিযোগে জেলে পুরে দেবে তার নিশ্চয়তা নেই । কেবল রাষ্ট্র নয়, বিভিন্ন গোষ্ঠীও বুদ্ধিজীবিদের খুন করতে ভয় পায় না । নকশাল নামে একদা বহু বুদ্ধিজীবি লোপাট হয়ে ছিলেন ; এখন ‘শহুরে নকশাল’ নামে কয়েকজনকে জেলে পোরা হয়েছে । ধর্মবাদীদের হাতে খুন হয়েছেন কর্ণাটক আর মহারাষ্ট্রের কয়েকজন বুদ্ধিজীবি ।
সমাজের যাঁরা নৈতিকতার জ্যাঠামশায়, তাঁরা সাহিত্যিকদের আত্মধ্বংসে সমাজেরই পচন দেখতে পান । বোদলেয়ার, ভেরলেন, র্যাঁবোর সময়ে ইউরোপের সমাজে ও রাজনীতিতে বিপুল রদবদল ঘটছিল, যা আমরা দেড়শো বছর পরে ভারতেও প্রত্যক্ষ করছি । এখন ইউরোপ আমেরিকায় ধর্মহীনতা ও যৌন-যথেচ্ছাচারকে অধঃপতন মনে করা হয় না, যা ভেরলেনের সময়ে করা হতো । ১৮৫৭ সালে বোদলেয়ারের ছয়টি কবিতাকে নিষিদ্ধ করার ঘটনা এখন ভারতীয় মাপকাঠিতেও হাস্যকর মনে হয় । ভেরলেনেরও মনে হয়ে থাকবে, যে, কবিতাগুলো কোন যুক্তিতে জনগণের নৈতিকবোধে আঘাত হেনেছে, যখন কিনা জনগণ নিজেরাই জীবনে বহু ঘটনা চেপে যায় । কলকাতায় কৃত্তিবাস গোষ্ঠীর বেশ কয়েকজন কবি অবিনাশ কবিরাজ লেনে যেতেন অথচ আত্মজীবনী লেখার সময়ে তা চেপে গেছেন । বোদলেয়ারের ছয়টা কবিতা থেকে নিষেধ তোলা হয় ১৯৪৯ সালে । অথচ তার কয়েক বছর পরেই দেখা দিয়েছিলেন আমেরিকার বিট জেনারেশনের কবিরা ; অ্যালেন গিন্সবার্গের ‘হাউল’ ঝড় তুলেছে । প্যারিস থেকে তার আগে ১৯৩৪ সালে প্রকাশিত হয়েছিল হেনরি মিলারের ‘ট্রপিক অব ক্যানসার’ । অতিযৌনতা, ভিক্ষাবৃত্তি, নেশা ইত্যাদি সত্বেও হেনরি মিলার নিজেকে অভিশপ্ত মনে করেননি ।
বোদলেয়ারের নিষিদ্ধ কবিতা ‘লিথি’, বুদ্ধদেব বসুর অনুবাদে :
উঠে আয় আমার বুকে, নিষ্ঠুর নিশ্চেতনা
সোহাগী ব্যাঘ্রী আমার, মদালস জন্তু ওরে
প্রগাঢ় কুন্তলে তোর ডুবিয়ে, ঘণ্টা ভরে,
চঞ্চল আঙুল আমার -- হয়ে যাই অন্যমনা ।
ঘাঘরায় গন্ধ ঝরে, ঝিমঝিম ছড়ায় মনে
সেখানে কবর খোঁড়ে আমার এ-খিন্ন মাথা,
মৃত সব প্রণয় আমার, বাসি এক মালায় গাঁথা
নিঃশ্বাস পূর্ণ করে কি মধুর আস্বাদনে !
ঘুমোতে চাই যে আমি যে-ঘুমে ফুরোয় বাঁচা,
মরণের মতোই কোমল তন্দ্রায় অস্তগামী
ক্ষমাহীন লক্ষ চুমোয় তনু তোর ঢাকবো আমি--
উজ্বল তামার মতো ও-তনু, নতুন, কাঁচা ।
শুধু তোর শয়ন ‘পরে আমার এ-কান্না ঘুমোয়,
খোলা ঐ খন্দে ডুবে কিছু বা শান্তি লোটে ;
বলীয়ান বিস্মরণে ভরা তোর দীপ্ত ঠোঁটে
অবিকল লিথির ধারা বয়ে যায় চুমোয় চুমোয় ।
নিয়তির চাকায় বাঁধা, নিরুপায় বাধ্য আমি,
নিয়তির শাপেই গাঁথি ইদানিং ফুল্লমালা ;
বাসনা তীব্র যতো, যাতনার বাড়ায় জ্বালা--
সবিনয় হায়রে শহিদ নির্মল নিরয়গামী !
এ-কঠিন তিক্ততারে ডোবাতে, করবো শোষণ
ধুতুরার নেশায় ভরা গরলের তীব্র ফোঁটায়
ঐ তোর মোহন স্তনের আগুয়ান দৃপ্ত বোঁটায়--
কোনোদিন অন্তরে যার হৃদয়ের হয়নি পোষণ ।
সমালোচকদের স্বীকৃতি পাচ্ছিলেন না বোদলেয়ার, ফলে যাত্রা আরম্ভ করেছিলেন আত্মক্ষয়ের গৌরবের পথে, তাঁর কবিতা সহজে কোনো পত্রিকা ছাপতে চাইছিল না, বোদলেয়ারের মনে হচ্ছিল অস্বীকার ও যন্ত্রণালাভের মধ্যে দিয়ে তাঁর স্খালন ঘটছে, কবিতায় ইতরতার সঙ্গে সৌন্দর্যের মিশেলে গড়া তাঁর পাঠবস্তুতে তিনি তাঁর প্রতি ঈশ্বরের অবিচারের প্রসঙ্গ তুলেছেন । তিনি এডগার অ্যালান পো-কে ফরাসী পাঠকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার সময়ে পো-এর জীবনেও মদ্যপানের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন, যা তাঁর জন্য হয়তো জীবনবিনাশী ছিল, কিন্তু তা তাঁকে করে তুলেছিল প্রকৃত সৃজনশীল মানুষ, কেননা, বোদলেয়ারের মতে, পো কখনও নেশাহীন প্রকৃতিস্হ থাকতে চাইতেন না । বদল্যার বলেছেন যে পো সাধারণ মানুষের মতন মদ খেতেন না, খেতেন বর্বরদের ঢঙে, মার্কিনী তেজে, যাতে এক মিনিট সময়ও নষ্ট না হয়, যেন তিনি খুন করার জন্য তৈরি, এমন একটা পোকাকে খুন করতে চাইছেন যা তাঁর ভেতরে বাসা বেঁধে আছে আর মরতে চায় না ।
বদল্যারের মতে, মত্ততা এডগার অ্যালান পো-কে কেবল যে মহান কবি করে তুলেছে, তা নয়, তাঁকে করে তুলেছে মহান মানুষ ; পো-এর মত্ততা ছিল স্মৃতিবর্ধনের ক্রোনোট্রোপ ( সময়/পরিসর ), সাহিত্যকর্মের খাতিরে একটি সুচিন্তিত ও স্বেচ্ছাকৃত উপায়, তা মারাত্মক দুর্দশাপূর্ণ হলেও, তাঁর স্বভাবচরিত্রের সঙ্গে খাপ খেয়ে গিয়েছিল । ভেরলেন যেমন বদল্যারের মাধ্যমে গড়ে তুলেছিলেন আত্মক্ষয়ের গৌরবের কিংবদন্তি, একই ভাবে বদল্যার আত্মক্ষয়ের গৌরবের কিংবদন্তি গড়ে তুলেছিলেন এডগার অ্যালান পো-এর মাধ্যমে ।
উনিশ শতকের ফ্রান্সে যে কবিদের রচনা আধুনিক বিশ্ব সাহিত্যকে রূপ দিয়েছে, তাঁদের প্রতি ফরাসি প্রাতিষ্ঠানিকতার দুর্ব্যবহার ব্যাখ্যার অতীত । ভেরলেন যাঁদের অভিশপ্ত কবি হিসাবে চিহ্ণিত করেছেন, তাঁদের সঙ্গে ভেরলেনের জীবনযাত্রা বেছে নেয়ায় পার্থক্য আছে । আবসাঁথের নেশার প্রতি ভেরলেনের টানের কারণ তিনি তাঁর ‘স্বীকৃতি’ বইতে জানাননি, এবং আবসাঁথ খাবার পর যে সমস্ত দানবিক আচরণ তিনি করতেন তারও কোনো ব্যাখ্যা নেই । অনেকে মনে করেন তাঁর বাবার পালিত মেয়ে এলিজা তাঁর সঙ্গে সঙ্গমের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের কারণে ভেরলেন হীনম্মন্যতায় ভুগতে আরম্ভ করেন এবং আত্মধ্বংসের দিকে এগিয়ে যান । পরবর্তীকালে তিনি তো যথেষ্ট রয়ালটি পেতেন এবং তা থেকে তিনি নিশ্চয়ই তাঁর পাঠকের সংখ্যাবৃদ্ধি আঁচ করে থাকবেন ।
র্যাঁবোর অভিশপ্ত হবার কারণ পাওয়া যায় বাবার অনুপস্হিতিতে । তাঁদের পাঁচ ভাইবোনের কারোর জন্মের সময়ে তাঁর বাবা বাড়িতে ছিলেন না । তাঁর যখন ছয় বছর বয়স তখন তাঁর বাবা তাঁদের ছেড়ে চলে যান, ফলে শৈশব থেকে তাঁকে আর তাঁর মাকে টিটকিরি শুনতে হতো। তাঁর মা নিজেকে বলতেন বিধবা । অনুপস্হিত বাবাকে ঈশ্বরের আসনে বসিয়ে র্যাঁবো ঈশ্বরনিন্দা ও খ্রিস্টধর্মকে আক্রমণ করেছেন তাঁর কবিতায় । ঈশ্বরই তাঁর ও তাঁর মায়ের দুঃখদুর্দশার জন্য দায়ি । সেই অনুপস্হিত বাবাকে তিনি প্যারিসের অগ্রজ কবিদের মধ্যে পেতে চেয়ে অবহেলিত হন ।
ভেরলেনও জেলে থাকার সময়ে রোমান ক্যাথলিক ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন, তবু তিনি ঈশ্বরভক্তি ও ঈশ্বরনিন্দার মাঝে দোটানায় পড়ে কবিতা লিখেছেন । খ্রিস্টধর্মের প্রফেটদেরও যেহেতু যন্ত্রণাভোগ করতে হয়েছে, যিশুকে ক্রূশকাঠে পেরেকে গেঁথা অবস্হায় ঝুলতে হয়েছে, তাই একজন কবিও, যে মানবসমাজের জন্য কবিতা লিখছে, তাকেও প্রফেটদের মতন অভিশপ্ত জীবন কাটাতে হবে, মনে করেছেন ভেরলেন । আঘাত পাওয়াকে তাঁরা অপরিহার্য সত্য বলে মান্যতা দিয়েছেন । রসাস্বাদন করেছেন শহিদত্বের, জাহির করেছেন তাকে । মন্দভাগ্যের সাধনা তাঁদের অন্তরজগতকে বড়ো বেশি দখল করে নিয়েছিল, বিশেষ করে ভেরলেনের । খ্রিস্টধর্মমতে মানসিক অবস্হানটি ‘ইপিফ্যানি’ । এই মনস্হতিকে অ্যারিস্টটল বলেছিলেন ‘দৈব উন্মাদনা’, ইউরোপীয় রেনেসাঁর গবেষক বলেছিলেন ‘শনিআক্রান্ত স্বভাবচরিত্র’।
যাঁরা আচমকা সেই ইপিফ্যানিতে আক্রান্ত হন, তাঁরা, ‘বিশুদ্ধ’ অভিজ্ঞতার খাতিরে, মনের ভেতরে সন্ধান করেন সীমাহীনতার, যে পরিসরে তিনিই নিজেকে মনে করেন সর্বেসর্বা, আত্মক্ষয় তাঁর কিচ্ছু করতে পারবে না ; মাদক, যৌনতা, মৃত্যু, ধর্মহীনতা, কোনো কিছুই তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারবে না, কেননা তিনি আত্মক্ষয়ের গৌরবে আহ্লাদিত পরিসরের সার্বভৌম মালিক । সেই গায়ক, কবি, চিত্রকর, ভাস্কর, স্হপতির আহ্লাদের শক্তিক্ষমতা, তাঁদের যন্ত্রণাদায়ক যাত্রাপথে এগোনোয় প্ররোচিত করে ; তাঁরা জানেন যে প্রয়াস না করলে তাঁরা কিছুই নন, তাঁরা একজন ‘নেইমানুষ’ ।
যৌনতা তাঁদের কাছে বংশরক্ষার অথবা সন্তানের জন্ম দেবার প্রক্রিয়া নয়, যেমন মাদক নয় নেশাগ্রস্ত থাকার জন্য, এগুলো তাঁদের ‘নেইমানুষ’ হতে দেয় না । বংশরক্ষা বা সন্তানোৎপাদনের যৌনতা, ব্যক্তিঅস্তিত্বকে ধারাবাহিকতার বাইরে নিয়ে যায়, গতানুগতিকতায় বেঁধে ফ্যালে। ধারাবাহিকতাহীনতা হলো অভিশপ্ত কবিদের প্রতিদিনের জীবনের সাধারণ স্বাভাবিক ঘটনা । জনসাধারণের মাঝে একজনের সঙ্গে আরেকজনের বাধা থাকে, অনেকসময়ে দূরতিক্রম্য, ধারাবাহিকতাহীনতা থাকে, পতিত-অঞ্চল থাকে । মানুষের ব্যক্তিএকক-বোধ জন্মায় তার সামনের বস্তুপৃথিবীর জিনিসগুলোর ব্যবহারের কারণে — তাদের দরুণ বস্তুদের থেকে সে বিচ্ছিন্ন থাকে । ‘নেই-বোধ’ হলো অস্তিত্বের ধারাবাহিকতা, এবং এই ধারাবাহিকতার সন্ধান করেন আত্মক্ষয়ের আহ্লাদে আক্রান্ত অভিশপ্ত কবিরা । ‘নেই-বোধ’ হলো অহং-এর সমাপ্তি, যা মানুষটি ঝেড়ে ফেলতে চাইছেন, এবং সেই কারণেই আশেপাশের জনসাধারণকে সরিয়ে দিতে চাইছেন ।
অমন মানুষটি আত্মবলিদানের গোমরে ভুগছেন কেন ? কেননা তাঁর কাছে আত্মবলিদানের গোমর হলো কেবলমাত্র ধ্বংস, তা নিশ্চিহ্ণ হওয়া নয় । আত্মবলিদানের গোমর বস্তুদের প্রতি আনুগত্যকে ধ্বংস করে ; প্রয়োজনীয় দৈনন্দিনের উপযোগীতাবাদী জীবন থেকে টেনে বের করে আনে, এবং মানুষটিকে প্রতিষ্ঠা করে দুর্বোধ্য খামখেয়ালে , স্বকীয় পবিত্রতায়, যার খোলোশা কেবল তিনিই করতে পারবেন । তাঁর এই ‘বিশুদ্ধ অভিজ্ঞতা’ ঘটে তাবৎ সীমাগুলোর বিদারের মাধ্যমে, যাবতীয় নিষেধ অতিক্রমের দ্বারা, যা তাঁকে একযোগে আহ্লাদ ও পীড়নের স্হিতিতে নিয়ে গিয়ে একাকী ছেড়ে দেয় । ‘বিশুদ্ধ অভিজ্ঞতা’ হলো ‘নেই-স্হিতি’, এবং সেহেতু মানসিক ও দৈহিক আত্মক্ষয় সম্পূর্ণ পরিবর্তন-পরিশীলনের জন্য একান্তই জরুরি । অভিশপ্ত কবির ভেতরে-ভেতরে যে সন্ত্রাস চলছে তা অন্য কেউ তাঁকে দেখে বুঝতে পারে না ; তার জন্য তাঁর গানে, সঙ্গীতে, কবিতায়, ভাস্কর্যে, পেইনটিঙে, স্হাপত্যে, প্রবেশ করতে হবে ।
ব্যক্তিএককের বিশুদ্ধ অভিজ্ঞতার ক্রোনোট্রোপে বাস্তব জগত আর মিথ মিলেমিশে গেলে তার যে মানসিক অবস্হা গড়ে ওঠে তাকে ভেরলেনের আলোচকরা বলেছেন ‘নুমিনাস’, যে অবস্হায় ব্যক্তিএককের অন্তরজগতে নিদারুণ তোলপাড় ঘটতে থাকে, সে তখন বাইরের জগতের প্রতি উৎসাহহীন, তার মনে হয় সে বাইরের জগতের দ্বারা অবদমিত, হতোদ্যম অবস্হায় সে নিজের ভেতরে আরও বেশি করে ঢুকে যেতে থাকে, তখন সে বিপজ্জনক আত্মক্ষয়ের স্বাদ পেতে আরম্ভ করেছে, খাদের কিনারে পৌঁছে গেছে, বুঝে উঠতে পারছে না ঝাঁপ দেবে নাকি ফিরে যাবে ।
সুইডেনের নাট্যকার অগাস্ট স্ট্রিণ্ডবার্গ, যিনি খাদের কিনারায় গিয়ে ফিরে এসেছিলেন, বেশ কিছু সময় মানসিক হাসপাতালে ছিলেন, তিনি নিজের অবস্হাটা যাচাই করে বলেছিলেন যে, ‘যারা উন্মাদ হবার সুযোগ পায় তারা যথেষ্ট ভাগ্যবান’ । মার্কিন কবি জন বেরিম্যান, যাঁর বাবা শৈশবে নিজেকে গুলি করে আত্মহত্যা করেছিলেন, এবং যিনি বাবার আত্মহত্যার স্মৃতি থেকে কখনও মুক্তি পাননি , বলেছিলেন, ‘যে কবি অত্যন্ত ভয়াবহ মানসিক চাপের মধ্যে দিয়ে গেছে, যা তাকে মেরে ফেলতে পারতো অথচ যা তাকে প্রকৃতপক্ষে বাঁচতে সাহায্য করেছে, তার অদৃষ্টের প্রশংসা করা উচিত’।
অভিশপ্ত কবির ভেতরে এক সৃজনশীল ক্ষমতা প্রবেশ করে ; সে চেষ্টা করে যায় যাতে বিস্ফোরণে সে নিজেই না উড়ে শতচ্ছিন্ন হয়ে যায়, সে চেষ্টা করে কখন সৃজনশীলতার আবেগ ও সংবেদনকে প্রয়োগ করতে হবে । সব সময় একটা ভীতি কাজ করে, কেননা সৃজনশীল মানুষটি খাদের ধার পর্যন্ত যাবেনই, আবার একই সঙ্গে তাঁর ভেতর এই ভীতি কাজ করে যে তিনি বড়ো বেশি মার্জিত রুচিশীল বিবেকী সুস্হতাবিশিষ্ট স্হিরমস্তিষ্ক হয়ে উঠছেন না তো ! সাধারণ মানুষের তুলনায় সৃজনশীল মানুষ, নিজের সৃজনশীলতার সঙ্গে আপোষ করতে না পেরে খানিকটা ম্যানিক-ডিপ্রেসিভ হয়ে পড়েন, এবং ম্যানিক-ডিপ্রেসিভ হবার কারণে তাঁরা যখন ডিপ্রেশানে আক্রান্ত হন তখন, সাধারণ মানুষের তুলনায়, অস্তিত্বের সমস্যাগুলোর মুখোমুখি হতে পারেন, অন্তদর্শী হতে পারেন, প্রতিক্ষেপক হতে পারেন । আমেরিকায় লেনি ব্রুস নামে একজন প্রতিসাংস্কৃতিক কমেডিয়ান ছিলেন, অশ্লীল ভাষায় সবায়ের সমালোচনা করতেন, যে কারণে তাঁকে কারাদণ্ড দেয়া হয়েছিল, এবং তাঁর মৃত্যুর পর তা মাফ করে দেয়া হয়, তিনি উন্মাদ বুদ্ধিমত্তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ, তাঁকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়নি, তিনি নিজেও আত্মক্ষয়ে ভোগেননি ।
ডাক্তারি ভাষায় আত্মক্ষয়ের গৌরবকে বলা হবেছে ‘হাইপোম্যানিয়া’ । কোনো সৃজনশীল মানুষকে যদি হাইপোম্যানিয়ার স্বীকৃতি দেয়া হয় তাহলে তাঁর কাছে তা সৃজনের স্বাধীনতাপ্রাপ্তি । সৃজনশীল মানুষ তাঁদের কাজের জন্য যে কাঁচা মাল ব্যবহার করেন, তা আসে তাঁদের অন্তর্জীবনের বুনিয়াদি বা আদিকালীন স্তর থেকে — যৌন কল্পনা, পূর্বপক্ষতা, আগবাড়া চারিত্র্য, বহুবিধ যৌনাঙ্গিকের ভাবনা থেকে । শৈশব থেকে মানুষের ভেতরে এই বোধগুলো কাজ করে, সে এই স্তরগুলো অতিক্রম করে যৌবনে পৌঁছোয় । বয়সের সঙ্গে সে আত্মনিয়ন্ত্রণ করতে শেখে, আদিম-চেতনাকে দাবিয়ে রাখতে শেখে, সামাজিক বাধানিষেধকে মান্যতা দিতে শেখে । কিন্তু সৃজনশীল মানুষ এগুলোর সংস্পর্শে থাকেন, আর তাদের বোঝার জন্য নিজের সঙ্গে লড়তে থাকেন, আর নিজের আদিম চারিত্র্যের সঙ্গে সংস্পর্শে থাকার অভিপ্রায়ে তিনি উন্মাদনা ও মতিস্হিরতার মাঝে ভারসাম্য বজায় রেখে চলেন আবার কখনও বা সেই ভারসাম্য হারিয়ে অভিশপ্ত হন।
তিন
পল-মারি ভেরলেনের জন্ম ১৮৪৪ সালের ৩০ মার্চ উত্তরপূর্ব ফ্রান্সের মোৎসেল আর সেইলি নদীর সঙ্গমস্হল মেৎজ শহরে । সমরবাহিনীর ক্যাপ্টেন তাঁর বাবা নিকোলাস অগুস্তে ভেরলেন ১৮৫১ সালে মেৎজ থেকে প্যারিসে পাকাপাকি বসবাসের জন্য চলে যান । সেখানে পল ভেরলেনকে বোনাপার্ত উচ্চবিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয় । স্কুলের তথ্য অনুযায়ী চোদ্দো বছর বয়সে তাঁকে দেখতে কুৎসিত মনে হতো । জীবনের প্রথম সাত বছর বাবার চাকুরির দৌলতে বিভিন্ন শহরে বসবাস করতে হয়েছিল ভেরলেনকে, যার দরুণ শৈশবে তাঁর একমাত্র বন্ধু ছিলেন তাঁদের বাড়িতে আশ্রয় নেয়া খুড়তুতো বোন এলিজা । এলিজার অকালমৃত্যু মেনে নিতে পারেননি কিশোর ভেরলেন ; এলিজা ছিলেন তাঁর প্রথম প্রেম, যদিও এলিজার বিয়ে হয়ে গিয়েছিল আর একটা বাচ্চা ছিল তবু ভেরলেন তাঁকে দৈহিকভাবে চেয়েছিলেন; এলিজাকে নিয়ে লেখা তাঁর ‘দুর্দান্ত উৎসব’ প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৬৯ সালে, এলিজার মৃত্যুর পর ।
১৮৬২ সালে স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ভেরলেন প্রথমে বীমা কোম্পানির চাকুরিতে যোগ দেন। ১৮৬৫ সালে তাঁর বাবা মারা যান । দুই বছর আইন পরীক্ষা পড়ার পর ছেড়ে দ্যান। ১৮৬৭ সালে এলিজা মোনকোঁলের মৃত্যুর ফলে তিনি নিজেকে নিঃসঙ্গ বোধ করতে থাকেন আর বেয়াড়া হয়ে যান, বাবা-মায়ের কাছে তাঁর আবদার বেড়ে যায়, খামখেয়ালি, অব্যবস্হিতচিত্ত, স্বার্থপর, অপরিণত যুবক হয়ে ওঠেন । তাঁর মা মদ খাবার টাকা যোগাতেন না বলে বাড়িতে প্রায়ই ঝগড়া হতো । উচ্চবিদ্যালয়ে পড়ার সময় থেকেই তাঁর আবসাঁথ খাবার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল । মদ্যপ অবস্হায় দু’বার মাকে খুন করার জন্য তাঁর পেছনে তরোয়াল নিয়ে দৌঁড়েছিলেন । ভেরলেনের বন্ধু তাঁদের দুজনের মাঝে গিয়ে ভেরলেনকে কাবু করেন । মাকে দ্বিতীয়বার আক্রমণের ব্যাপার চলেছিল সাত ঘণ্টা কথা কাটাকাটির মাঝে । মা পরের দিন সবকিছু ভুলে গিয়ে আদরের ছেলেকে ক্ষমা করে দিতেন ।
শার্ল বোদলেয়ারের ‘পাপের ফুল’ ( Les fleurs du mal ) পড়ার পর পল ভেরলেনের কবিতা লেখার ইচ্ছা হয়। ১৮৬৩ সালে তাঁর প্রথম কবিতা ‘মসিয়ঁ প্রুধোম’ প্রকাশিত হয় । তিনি ‘সমসাময়িক কবিতা’ ( Le Parnasse Contemporain ) পত্রিকার সম্পাদক কাতুলে মেনদেস-এর সঙ্গে দেখা করেন । পত্রিকাটিতে তাঁর আটটি কবিতা প্রকাশিত হয় । উনিশ শতকের ফ্রান্সে একদল কবি আরম্ভ করেন পারনাসিয় আন্দোলন ; নামটি নেয়া হয়েছিল অ্যাপোলো আর মিউজদের পবিত্র গ্রিক পাহাড়ের নাম থেকে । পারনাসিয়রা বিষয়বস্তু এবং শৈলীর বিস্তার প্রদর্শন করলেও, তাঁরা গুরুত্ব দিয়েছেন কারিগরি, অশেষ সৌন্দর্য ও বস্তুনিষ্ঠাকে। রোমান্টিসিজমের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসাবে দেখা দিয়েছিল পারনাসিয় আন্দোলন এবং তা ক্রমে প্রসারিত হয় প্রতীকবাদ ও ডেকাডেন্ট কাব্যিক ঐতিহ্যে । পারনাসিয় আন্দোলনের প্রধান কবি বলে মনে করা হয় শার্ল-মারি-রেনে লেকঁত দ্যলিজেকে, কিন্তু আন্দোলনের অংশ হিসাবে মান্যতা দেয়া হয় থিয়োদোরে দ্যবাঁভিল, অঁরি কাজালিস, ফ্রাঁসোয়া কোপি, আনাতোল ফ্রাঁসে, থিয়োফিল গতিয়ে, জোসে-মারিয়া দ্যহেরদিয়া, সালধ প্রুধোম, পল ভেরলেন ও শার্ল বোদলেয়ারকে। ১৮৬৬, ১৮৭১ ও ১৮৭৬ সালে সবসুদ্ধ নিরানব্বুইজন কবির তিনটি সংকলন প্রকাশ করেন আলফোঁসে লেমেরে, কাতুলে মেন্দেস আর লুই জেভিয়ার । এই তিনটি সংকলনের প্রকাশকে ফরাসী সাহিত্যে বাঁকবদলকারী ঘটনা বলে মনে করা হয় । তবে থিয়োফিল গতিয়ে যখন ‘আর্ট ফর আর্টস শেক’ স্লোগান দিলেন তখন পারনাসিয় কবিরা একটা বৌদ্ধিক গতিমুখ পেলেন । ভেরলেন নিজেকে পারনাসিয় আন্দোলনের একজন সদস্য বলে মনে করতেন না ।
১৮৬৬ সালে প্রকাশিত হয় ভেরলেনের প্রথম কাব্যগ্রন্হ Poemes Saturniens এবং দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্হ Gallant Parties প্রকাশিত হয় ১৮৬৯ সালে । মেনদেসের মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে অন্যান্য পারনাসিয় কবি লেকঁতে দ্যলিজে, থিয়োদির দ্য বাঁভিল, লুই জেভিয়ার দ্য রিকার্দ, ফ্রাঁসোয়া সিপ্পি প্রমুখের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় এবং সুফলো রোড-এর সস্তা মদের দোকানে সবাই মিলে আড্ডা দিতেন । বিয়ারের স্বাদ সেসময়ে ভালো ছিল না বলে আবসাঁথের প্রতি আসক্ত হন ভেরলেন ও অন্যান্য কবিরা । ভেরলেন নিজেই ‘স্বীকৃতি’ বইতে জানিয়েছেন যে তিনি একবার সারারাতে দুশোবার অর্ডার দিয়ে আবসাঁথ খেয়েছিলেন । Poemes Saturniens এর “হেমন্তের কবিতা” লিখে ভেরলেন কবিদের প্রশংসা পেয়েছিলেন এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে এই কবিতাটির প্রথম ছয় লাইন মিত্রপক্ষের সৈন্যবাহিনী নরম্যাণ্ডি অবতরণের কোড হিসাবে বিবিসি থেকে প্রসার করেছিলেন ; প্রথম তিন লাইন পয়লা জুন আর দ্বিতীয় তিন লাইন পাঁচুই জুন :
হেমন্তের বেহালার
দীর্ঘ ফোঁপানিগুলো
আমার হৃদয়কে আহত করে
একঘেয়ে সুরের অবসাদে ।
সমস্তকিছু শ্বাসহীন
আর ফ্যাকাশে, যখন
সময়ের কাঁসর বেজে ওঠে,
আমার মনে পড়ে
বিগত দিনগুলো
আর আমি কাঁদি
আর আমি চলে যাই
এক অশুভ বাতাসে
যা আমাকে নিয়ে যায়
এখানে, সেখানে,
যেন গাছের এক
মৃত পাতা ।
বাইশ বছর বয়সে লেখা কবিতাটির শিরোনাম যদিও ‘হেমন্তের গান’, প্রতীকবাদী অন্যান্য কবিদের মতো ভেরলেনও, র্যাঁবোর সঙ্গে পরিচয়ের আগে, ‘আর্ট ফর আর্ট সেক’কে মান্যতা দিয়ে কবির অন্তরজগতকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন এবং তিনি যে বলতেন কবিতাকে সঙ্গীতময় হয়ে উঠতে হবে, তার পরিচয় মেলে এই কবিতায় ; তিনি বলতেন যে কবিতায় সঙ্গীতই প্রথম এবং প্রধানতম । যাঁরা কবিতাটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন, তাঁদের বক্তব্য, ফরাসি ভাষায় না পড়লে কবিতাটির সঙ্গীতময়তা অনুধাবন করা যায় না । এই কবিতাটির অনুকরণে উনিশ শতকের শেষ দিকে বহু কবি কবিতা লিখেছেন । এই কবিতার আনুয়ি বা অবসাদ হয়ে ওঠে ভেরলেনের কবিতার বৈশিষ্ট্য। ভেরলেনের কবিতায় ক্ষয় বা অপচয় ঘুরে-ঘুরে এসেছে । কবিতাটির ধীর লয় কবির অবসাদকে তুলে ধরার জন্য প্রয়োগ করেছেন ভেরলেন । পারনাসিয় কবিদের প্রভাবে র্যাঁবো ‘দি ড্রাঙ্কন বোট’ বা ‘মত্ত নৌকো’ নামে একটা কবিতা লিখেছিলেন, কিন্তু পরে নিজেই এই কবিতার ধারাকে সমর্থন করেননি, এবং গদ্যকবিতার দিকে ঝোঁকেন ।
উনিশ শতকের প্যারিসে লাতিন কোয়ার্টার ছিল যেন এক বোহেমিয়ান দ্বীপ, যেখানে জড়ো হতেন অজস্র লেখক, শিল্পী, নাট্যকার আর কবিযশোপ্রার্থী । ভিক্তর য়োগো, শার্ল বোদলেয়ার প্রমুখের মতন পল ভেরলেনও বেছে নিয়েছিলেন এলাকাটা, সস্তার মদ আর বেশ্যাসঙ্গের আকর্ষণে । প্যারিসের ইতিহাসে এই সময়টাই ছিল প্যারিস কোয়ার্টারের খ্যাতি-কুখ্যাতির কারণ -- এখন তা একেবারে বদলে গিয়েছে । যারা এই এলাকায় বাস করতো তাদের কাছে পাড়াটা ছিল নরক । অত্যন্ত গরিব শ্রমজীবিদের পাড়া, দুবেলা খাবার জোটেনা, অসুখে পড়লে বিনা চিকিৎসায় মারা যেতে হয় ইত্যাদি । তারা প্রধানত গ্রামাঞ্চল থেকে এসে সস্তায় থাকার জায়গা হিসাবে বেছে নিয়েছিল পাড়াটা, আর বাড়তি রোজগারের জন্য ঘর ভাড়া দিতো, বেশ্যাগিরি করতো, সস্তার মদ বিক্রি করতো । ক্রমশ তারা লেখক-কবি-শিল্পীদের চাহিদা মেটাবার জন্য সারারাতের যৌনহুল্লোড়ের ব্যবস্হা করতো । ফরাসি সাহিত্যে দেখা দিচ্ছিল রোমান্টিক ঔপন্যাসিকদের জনপ্রিয়তা, আদর্শের পরিবর্তে ‘পাপের ফুলের’ বা ‘নরকে ঋতুর’ প্রতি আকর্ষণ । ফাউস্তের জায়গা নিয়ে নিচ্ছিল মেফিসতোফিলিস । ঈশ্বর-বিশ্বাস নিয়ে দোটানায় ছিলেন কবি-লেখক-শিল্পীরা । পেত্রুস বোরেল নামে এক কবি, যিনি বোদলেয়ারের বন্ধু ছিলেন, লাতিন কোয়ার্টারে গরিব সেজে ঘুরে বেড়াতেন, তাঁকে বলা হতো “নেকড়ে বাঘে পরিণত মানুষ।”
ভেরলেনের মতিগতি ফেরাবার জন্য তাঁর মা তাঁর বিয়ে প্রথমে ঠিক করেন কড়া মেজাজের এক মামাতো বোনের সঙ্গে, কিন্তু তা এড়াবার জন্য ভেরলেন পছন্দ করেন এক বন্ধুর সৎবোন, তাঁর চেয়ে বয়সে বেশ ছোটো সুন্দরী তরুণী মাতিলদে মত দ্য ফ্ল্যেওরভিলেকে, বিয়ে হয় ১৮৭০ সালে ; মাতিলদের সঙ্গে পরিচয়ের সময়ে যুবতীটির বয়স ছিল ষোলো, তাঁর মা-বাবা ভেরলেনকে জানান যে তাঁকে এক বছর অপেক্ষা করতে হবে । ১৮৬৯ সালের জুনমাসের এক দুপুরে, মদ খাবার জন্য বন্ধু শালর্ক দ্য সিভরির মমার্তর বাড়িতে গিয়েছিলেন পল ভেরলেন । শার্ল তাঁর মা আর সৎবাবা থিওদোর মতে দ্য ফ্লেওরভিলের সঙ্গে থাকতেন । দুই বন্ধু যখন গল্প করছিলেন তখন ষোলো বছরের একটি সুন্দরী যুবতী ঘরে ঢোকেন, ভেরলেনের মতে ইচ্ছাকৃতভাবে ঢোকেন, তিনি শার্লের সৎবোন মাতিলদে মতে । ভেরলেনের কবিতা তাঁর পড়া ছিল এবং পড়ে কবিকে ভালো লেগেছিল, তিনিও ভেরলেনের প্রেমে পড়েন । বিয়ের ছয় মাসের মধ্যেই মাতিলদে গর্ভবতী হবার দরুন ভেরলেন বিষাদে আক্রান্ত হয়ে আবার লাতিন কোয়ার্টারে যাতায়াত আরম্ভ করেন ।তাঁদের একটি ছেলেও হয় ।
মাতিলদে এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন যে প্রথম দুই বছর ভেরলেন তাঁকে খুব ভালোবাসতেন এবং তাঁকে নিয়ে অনেক কবিতা লিখেছিলেন। ভেরলেনের তৃতীয় কাব্যগ্রন্হ ‘ভালো গান’-এর কবিতাগুলো মাতিলদেকে মনে করে লেখা । কিন্তু মাঝে-মাঝে ভেরলেনের রুদ্ররূপ বেরিয়ে পড়তো আর তিনি মাতিলদের গায়ে হাত তুলতেন । একবার তিনি মাতাল অবস্হায় তাঁর ছেলে জর্জকে তুলে দেয়ালে মাথা ঠুকে দিয়েছিলেন । তাঁর মা, শশুর-শাশুড়ির উপস্হিতিতেও এরকম আচরণ করতেন তিনি ।
ভেরলেন মিউনিসিপালিটির সরকারি চাকরিতে যোগ দেন ১৮৭০ সালে । কিন্তু তৃতীয় নেপোলিয়ানের পতনের পরবর্তী দ্রোহের সময়ে প্যারিস-শহর ও চাকরি ছেড়ে পালান । ১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৭০ থেকে ২৮ জানুয়ারি ১৮৭১ পর্যন্ত প্রুসিয় সেনারা প্যারিস শহর ঘিরে ফরাসিদের জব্দ করতে চায় । সমস্ত কিছুর অভাব দেখা দেয় । কবি-লেখকরা লাতিন কোয়ার্টারের যে পাড়ার পানশালায় গিয়ে আড্ডা দিতেন সেখানেের ভোজন-তালিকায় ঘোড়া, কুকুর, বিড়াল এমনকি ইঁদুরের মাংস বিক্রি হতো । নারী আর পুরুষ বেশ্যারা এই খাবার একপেট খাবার বিনিময়ে সঙ্গমে রাজি হয়ে যেতো । এই সময় খবর রটে যায় যে বিসমার্ক পরামর্শ দিয়েছেন প্যারিসের ওপরে চারিদিক থেকে কামান দাগা হোক, কিন্তু ব্লুমেনথেল তা সামলে দেন এই তর্কে যে ফরাসি সেনার বদলে সাধারণ মানুষ তাতে মারা পড়বে । ভেরলেনসহ অনেকেই, যাঁরা প্যারিস কমিউনে যোগ দিতে চাননি, তাঁরা প্যারিস ছেড়ে পালান । ভেরলেন অবশ্য কমিউনের প্রেস অফিসার হিসাবে ১৮৭০-এ কাজ করেছিলেন আর কমিউন ভেঙে যাবার পর রাস্তায়-রাস্তায় খণ্ডযুদ্ধ আরম্ভ হলে অন্যান্য কবি-লেখকদের সঙ্গে গা ঢাকা দেন ।
পল ভেরলেনের জীবনযাত্রা, অপরাধ আর সাধাসিধে ছলাকলাশূন্যতার মাঝে দোল খেয়েছে । স্তেফান মালার্মে ও শার্ল বোদলেয়ারের সঙ্গে তাঁকে প্রতীকবাদী কবিতার ত্রিমূর্তির অন্তর্গত করলেও, দুটি প্রতীতি প্রাধান্য পায় : প্রথম হল যে কবির অহং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ; দ্বিতীয় যে কবিতার কাজ হল চরম সংবেদন ও একক ধৃতির মুহূর্তগুলোকে অক্ষুণ্ণ রাখা । Poemes saturniens ( ১৮৬৬ ) কাব্যগ্রন্হে তিনি প্রশ্ন তুলেছিলেন, “একে মিলোর তৈরি ভেনাস বলা হবে নাকি নিছক শ্বেতপাথর ?” তাঁর কবিতায় আপাত-অনিশ্চয়তা ও অস্পষ্টতা সত্বেও, তিনি কবিতার কারিগরিতে সহজ ও সঙ্গীতময় শব্দ প্রয়োগ করে সাবধানি কারুনৈপূণ্য বজায় রেখেছেন । ফরাসি ধ্রুপদি কবিতার খোলোসের মধ্যে থেকেও ছন্দবর্জনের খেলা খেলেছেন, যেমন ১৮৭৪-এ রচিত Romances sans Paroles কবিতায় লিখেছেন :
“আমার হৃদয়ে ক্রন্দন
শহরে বৃষ্টি পড়ার মতো”
মাতিলদেকে নিয়ে ভেরলেন ভালোবাসার অনেকগুলো কবিতা লিখেছিলেন Le bonne chanson ( The Good Song ) কাব্যগ্রন্হে । কয়েকটার বাংলায়ন :
এক নারীসন্ত তাঁর জ্যোতিতে
এক নারীসন্ত তাঁর জ্যোতিতে,
এক গিন্নিমা তাঁর মিনারে,
মহিমা ও ভালোবাসা
যা মানুষের শব্দাবলীতে আছে ;
সোনার বার্তা যা বাঁশি
বহুদূরের বনানী থেকে বাজায়,
অবলা গর্বের সঙ্গে বিবাহিত
যা বহুকাল আগের মহিমাময়ীদের ;
তার সাথে, ধরা পড়ে না এমন সৌন্দর্য
এক তরতাজা বিজয়িনী হাসির
যা ফুটে উঠেছে রাজহাঁসের পবিত্রতায়
আর এক নারী-শিশুর লজ্জায় ।
মুক্তার মতো আদল, শাদা আর গোলাপি,
এক মৃদু অভিজাত স্বরসঙ্গতি :
আমি দেখি, আমি এই সবকিছু শুনতে পাই
মেয়েটির শার্লমেনিয় বংশধরের নামে ।
আমি অধর্মের পথে গিয়েছিলুম ...
আমি অধর্মের পথে গিয়েছিলুম,
বেদনাদায়ক অনিশ্চিত
তোমার প্রিয় হাত ছিল আমার পথনির্দেশক।
তাই দূরে দিগন্তের উপর ফ্যাকাশে
ভোরের একটি দুর্বল আশা ছড়াচ্ছিল দ্যুতি;
তোমার দৃষ্টিতে ছিল ভোর।
চারিদিক নিঃশব্দ, তোমার সুরেলা পদক্ষেপ ছাড়া শব্দ নেই,
ভ্রমণকারীকে উত্সাহিত করেছো তুমি।
তোমার কন্ঠস্বর আমাকে বলেছিল: "এগিয়ে চলো !"
আমার ভয়ঙ্কর হৃদয়, আমার ভারী হৃদয়
একা কেঁদেছিল দুঃখের পথযাত্রায়
ভালবাসা, আনন্দদায়ক বিজয়ী,
আমাদের আনন্দের বাঁধনে আবার একত্র করেছে।
১৮৬৫ সালে শার্ল বোদলেয়ার সম্পর্কে লেখা দুটি প্রবন্ধে ভেরলেন জানিয়েছিলেন যে একজন কবির অন্বেষন কেবল সৌন্দর্য । কবিতা রচনায়, তিনি বলেছেন, প্রেরণা আর আবেগের যৎসামান্য স্হান থাকলেও কবির থাকা দরকার কারিকুরির সৃষ্টিশীলতা । ব্যক্তিগত আবেগকে যদি ব্যবহার করতে হয় তাহলে ছন্দ, ধ্বনি এবং চিত্রকল্পকে একত্রিত করে একটি কাব্যিক সঙ্গীত গড়ে নিতে হবে এবং সেই জগতে কোনোকিছুই আপতনিক নয় । ভেরলেনের কারিগরির ফল হল তাঁর কবিতার সঙ্গীতময়তা ; ধ্বনিরা একত্রিত হয়ে এক সুরেলা ঐকতান সৃষ্টি করে । ১৮৮২ সালে তিনি বলেছিলেন, “L’Art poetique” কবিতায়, “কবির উচিত বিজোড়-মাত্রার পঙক্তি, যথাযথ-নয়-এমন শব্দভাঁড়ার এবং প্রচ্ছন্ন চিত্রকল্প ব্যবহার করা ; রঙের বদলে অতিসূক্ষ্ম তারতম্যকে গুরুত্ব দেয়া । কবিকে ইচ্ছাকৃত ছন্দ, বৈদগ্ধ্য ও বাগ্মীতা এড়াতে হবে । কবিতা হবে হালকা, বাতাসে ভাসমান, যৎসামান্য সুগন্ধময় ও ক্ষণিক । এছাড়া সমস্তকিছু কবিতা হয়ে ওঠার পরিবর্তে হয়ে উঠবে সাহিত্য ।”
সমসাময়িক বাস্তববাদ এবং বাগাড়ম্বরপূর্ণ অলঙ্কার বর্জন করে অন্যান্য প্রতীকবাদী কবিদের মতো পল ভেরলেনও উদ্দীপিত করতে চেয়েছেন মেজাজ, সত্তা । তাঁর কাব্যগ্রন্হ Fetes gallantes এর অন্তর্গত Clair de Lune ( Moonlight ) “চাঁদের আলো” কবিতাটিকে মনে করা হয় তাঁর সবচেয়ে ভালো কাজ । যেভাবে চাঁদ তার আলো সূর্য থেকে পায়, ভেরলেন চাইলেন এমন বিষয়বস্তু বেছে নিতে যা সহজে অভিগম্য নয়, তাই চাঁদের মতো পরোক্ষভাবে বিষয়বস্তুকে দীপ্ত করতে চাইলেন, যা প্রতিফলন সৃষ্টি করে ।
ভেরলেনের কবিতাটিতে আছে মুখোশ আর নৃত্য, অভূতপূর্ব ছদ্মবেশ, আহ্লাদিত ঝর্ণাদের ফোঁপানি, চাঁদের আলো : বিশেষকিছু না বলেই কবিতাটিতে ইশারামূলক ছবির স্লাইড চলে যায় একের পর এক । ডেভিড ওইসত্রাখ ও ফ্রিদা বাওয়ের এই কবিতাটিকে নিয়ে একটি নৃত্যনুষ্ঠান করেছেন । ক্লদ দেবুসি, রেনাল্দো হাহন, পোলদোস্কি, গুস্তাভ কার্পেন্তিয়ের এবং গ্যাব্রিয়েল ফাওরে নিজেদের মতো করে সুর দিয়েছেন কবিতাটিতে । ইংরেজিতে যাঁরা অনুবাদ করেছেন তাঁরা বলেছেন কবিতাটি অনুবাদ করা কঠিন।
Moonlight
Your soul is like a landscape fantasy,
Where masks and Bergamasks, in charming wise,
Strum lutes and dance, just a bit sad to be
Hidden beneath their fanciful disguise.
Singing in minor mode of life's largesse
And all-victorious love, they yet seem quite
Reluctant to believe their happiness,
And their song mingles with the pale moonlight,
The calm, pale moonlight, whose sad beauty, beaming,
Sets the birds softly dreaming in the trees,
And makes the marbled fountains, gushing, streaming--
Slender jet-fountains--sob their ecstasies.
আমি এখানে শুভদীপ নায়কের করা বাংলা অনুবাদ দিলুম । উনি নামকরণ করেছেন ‘জ্যোৎস্না’
জ্যোৎস্না
( clair de lune / Moonlight)
তোমার অন্তর এক প্রশস্ত কল্পনার মতো
সেখানে মুখোশ ও মুখশ্রী দুই-ই প্রজ্জ্বলিত
বীণার তার এবং নৃত্য, যা আসলে বেদনামথিত
তোমাকে লুকিয়ে রাখে সৌন্দর্যের আড়ালে
সঙ্গীতকে ধীরে ধীরে করে তোলো বৃহৎ জীবন
ভালবাসাময়, নিশ্চল ও শান্ত
তাদের সুখের ওপর বজায় রাখো বিশ্বাস
সেইসব সঙ্গীত তুমি ধরে রাখো জ্যোৎস্নায়
শান্ত পরাভব সেই জ্যোৎস্না, অপূর্ব ক্লেশে বিকশিত
পাখিদের মতো এসে বসে স্বপ্নময় গাছের ডালে
হয়ে ওঠে ঝর্ণা, চিত্তের প্রবাহ
ঝর্ণার ঋজুতায়, -- নিজস্ব উল্লাসে
একজন মানুষের আত্মার রুপকশোভিত ছবিতে, ‘চাঁদের আলো’ জাগিয়ে তোলে সৌন্দর্য, ভালোবাসা আর প্রশান্তির আকাঙ্খা । কবিতাটি থেকে ক্রমবর্ধমান হতাশার যে আবহ গড়ে ওঠ তাতে পাওয়া যায় ভেরলেনের আত্মমগ্নতার কন্ঠস্বর । ভেরলেন পাঠকের মনে সন্দেহ তৈরি করতে চেয়েছেন, যাতে সে ভাবতে বাধ্য হয়, বাস্তবে কি সত্যিই ভালোবাসা আর আনন্দ পাওয়া সম্ভব । প্রধান উপমাটিকে প্রয়োগ করে তিনি বলতে চেয়েছেন যে প্রত্যেক মানুষই তার অন্তরজগতে একটা ভূদৃশ্য বহন করে, আর এই ক্ষেত্রে, যে উপাদান তৈরি হয় তা হলো একই সঙ্গে সুন্দর আর আশাহীন । অস্তিত্ব এবং যা দেখা যাচ্ছে, তার বৈপরীত্য কবিতাটির গুরুত্বপূর্ণ থিম । দৈহিক সৌন্দর্য আর বিষাদের মিশ্রিত অবস্হান ভেরলেন পেয়েছেন নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে । তাঁর মতে, মানুষের জীবনে এবং আত্মায়, অর্থাৎ মৃত্যুর পর, তার নিখুঁত হবার প্রয়াস কখনও পুরণ হবে না । জীবনের সত্যকার সত্তা উপরিতলে পাওয়া যাবে না ।
ভেরলেনের সযত্নে রচিত কবিতার বনেদ প্রায়শই তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতানির্ভর, নিঃসন্দেহে নাটকীয় এবং আবেগমথিত বিষয়বস্তু । তাঁর “Poemes saturniens” প্রস্তাবনায় স্পষ্ট যে তিনি নিজের অবজ্ঞাত, দৈন্যপীড়িত, দুর্দশাগ্রস্ত নিয়তি আঁচ করতে পেরেছিলেন । এই কাব্যগ্রন্হের সব কয়টি কবিতায় তিনি তুলে ধরেছেন অসুখী থাকার স্বপূরক প্রত্যাশার একাধিক বিন্যাস । আনন্দের ক্ষণিক মুহূর্ত ভেরলেনের সমস্ত কবিতায় ছেয়ে আছে । এমনকি “Sagesse” গ্রন্হে, যেখানে রোমান ক্যাথলিক রহস্যময়তার কথা বলেছেন, এবং বলেছেন যে তাতেই আছে সর্বোচ্চ আনন্দ, ঈশ্বরের সঙ্গে শান্তিময় আলাপনের সময়েও তিনি অধঃপতনের সময় ফিরে আসার ভয়ে আতঙ্কিত । যেহেতু যৌনতা, ঈশ্বর আর আবসাঁথ তাঁর ‘শনিআক্রান্ত নিয়তি’ থেকে মুক্তি দিতে পারেনি, তাই তাঁকে শেষ পর্যন্ত অন্য আশ্রয় খুঁজতে হয়েছে, এবং তা হল ঘুম । শেষ দিকের কবিতায় বারে বারে ঘুরেফিরে এসেছে ঘুমের কথা, চিত্রকল্পগুলো ঘুমের, যেন কমনীয় ঘুমপাড়ানি গানের মনোরম ছবি -- তা থেকে রঙ, হাসি, তীক্ষ্ণতা, জমকালো, মাত্রাধিক ধ্বনি বাদ দেয়া হয়েছে -- কবির ক্ষতবিক্ষত মনকে ঘুমের আরামে শান্তি দিতে পারে । বেশ কিছু কবিতায় এক মাতৃমূর্তিকে পাওয়া যায় দোলনার পাশে কিংবা এক মাতৃমূর্তি লক্ষ রাখেন ঘুমন্ত কবির পাশে দাঁড়িয়ে । যে কবিতায় ঘুমের মোটিফ নেই, তাতেও কবিতার শেষের পঙক্তিগুলোয় এসেছে মুছে যাবার রিক্ততাবোধ ।
আলোচকরা ভেরলেনকে তাঁর কবিতার শিল্পানুগ ও গভীর অনুভূতির বৈশিষ্ট্যের কারণে ফরাসী প্রতীকবাদের অগ্রদূতদের একজন হিসাবে চিহ্ণিত করলেও, তিনি তাঁর কবিতাকে ডেকাডেন্ট বা প্রতীকবাদের তকমা দিতে অস্বীকার করে বলেছেন যে তিনি নিজেকে একজন ‘ডিজেনারেট’ বা অপজাত কবি বলতে চাইবেন, কেননা তাঁর কবিতায় থাকে অহংকার ও অরাজকতার প্রবণতা ; প্রতীকবাদীদের তুলনায় তিনি প্রচলিত ভাষাকে সঙ্গীতময় করেছেন তাঁর কবিতায়। প্রকৃতপক্ষে ভেরলেনের জীবনের ঘটনাবলী ছেয়ে ফেলেছে তাঁর কবিতার গুণাগুণ ও কাব্যিক প্রতিভা । যেমন তাঁর জীবনে, তেমনই তাঁর কবিতায়, অবিরম লড়াই দেখা যায় তাঁর অন্তরজগতের সঙ্গে তাঁর ইন্দ্রিয়ের, লাম্পট্য ও পশ্চাত্যাপের । তাঁর চরিত্রকে আক্রমণ সত্বেও, ভেরলেনকে মনে করা হয় একজন সুসম্পূর্ণ কবি, যাঁর অসাধারণ প্রতিভা দেখা যায় কবিতার অঘনিভূত মাত্রায়, ইশারামূলক ও লাক্ষণিক ভাষায় এবং প্রতিচ্ছায়াময় বাক্যালঙ্কারে । ফরাসি কবিতাকে ভেরলেনই পরিভাষাগত প্রাবল্যের বাইরে বের করে আনেন এবং ফরাসী ভাষার সহজাত সঙ্গীতময়তাকে ব্যবহার করা আরম্ভ করেন । তিনি বলেছেন কবিতা হওয়া উচিত সুখশ্রাব্য ও সন্মোহক, অস্পষ্ট ও দ্রবনীয় ; পাঠক কবিতাকে বিভিন্ন থিমে চিহ্ণিত করতে পারবেন, এমন কবিতা লেখা তিনি পছন্দ করেন না । সেকারণেই তাঁর কবিতার অনুবাদে তাঁকে সম্পূর্ণ পাওয়া যায় না। তাঁর বক্তব্য বোঝাবার জন্য ভেরলেন কবিতার শিল্প (Art Poetique ) শিরোনামে একটি কবিতা লিখেছিলেন ; আমি বাংলায়নের চেষ্টা করেছি :
সবকিছুর আগে সঙ্গীতময়তা--
আর এর জন্য আরও অস্বাভাবিকতা--
অস্পষ্ট ও আরও বেশি বাতাসে মিলিয়ে যাওয়া,
তাকে ভার বইতে হয় বা বেঁধে ফেলতে হয় তাকে বাদ দিয়ে দাও
তাকে এমন হতে হবে যে তুমি খুঁজে বেড়াবে
তোমার শব্দগুলোয় কোনোরকম গাফিলতি ছাড়াই :
ধূসর গান ছাড়া প্রিয় আর কিছু নেই
যেখানে বিচলন ও যথাযথের মিল হয় ।
আনেকটা কালোজালের আড়ালে সুন্দর চোখের মতন,
অনেকটা ছড়িয়ে-পড়া দুপুরের স্পন্দনের মতন,
অনেকটা ( যখন হেমন্তের আকাশ শোভনীয় করে তোলে )
সুস্পষ্ট নক্ষত্রদের নীল বিশৃঙ্খলা !
কেননা আমরা আরও বেশি চাই সূক্ষ্ম তারতম্য--
রঙ নয়, সূক্ষ্ম তারতম্য ছাড়া কিছু নয় !
ওহ ! কেবল সূক্ষ্ম তারতম্য নিয়ে আসে
স্বপ্নকে স্বপ্নের মধ্যে আর বাঁশিকে শিঙায় !
খুনির ধারালো বক্তব্য থেকে দূরে রাখো,
নিষ্ঠুর বৈদগ্ধ আর পঙ্কিল হাসি,
যা নীল শূন্যতার চোখে অশ্রূজল এনে দ্যায়---
আর মৃদু আঁচের যাবতীয় রসুনরান্না ।
বাগ্মীতাকে ধরে তার ঘাড় মুচড়ে দাও !
তোমার তাতে ভালো হবে, কর্মচঞ্চল মেজাজে,
যাতে কবিতার মিলকে কিছুটা সুবিচার করা যায় ।
যদি না লক্ষ রাখা হয়, তাহলে তা কোথায় যাবে ?
ওহ, কে আমাদের বলতে পারে মিলের ভ্রষ্ট আচরণ ?
কোন বধির বালক কিংবা উন্মাদ কালো মানুষ
আমাদের জন্য বানিয়েছে এই এক পয়সার খেলনা,
যা ফাঁপা শোনায় আর শুনে মনে হয় নকল
সঙ্গীতকে হয়ে উঠতে দাও, অনেক বেশি করে আর সবসময় !
তোমার কবিতা হয়ে উঠুক চলমান জিনিস
যাকে অনুভব করে মনে হবে তা বদলে যাওয়া আত্মা থেকে পালিয়ে যাচ্ছে,
অন্য আকাশ থেকে অন্য প্রেমের দিকে ।
তোমার কবিতাকে আনন্দময় ঘটনা হয়ে উঠতে দাও,
অস্হির ভোরের বাতাসের মাঝে,
যা পুদিনা আর থাইমলতার সুগন্ধ নিয়ে উড়ে বেড়ায়…
আর বাদবাকি সমস্তই সাহিত্য ।
ফ্রান্সে, রোমান্টিসিজমের পর, তখন রোমান্টিসিজম বলতে যা বোঝাতো, আর পারনাসিয়দের দ্ব্যর্থহীন, ধ্রুপদি, অতিরিক্ত যত্নবান, চিত্তাকর্ষকভাবে মোহনীয় কবিতার যুগের পর, সমাজ যখন কলকারাখানার আধুনিকতাবাদী সমাজে অনিশ্চিত জীবনযাপনের মুখোমুখি হওয়া আরম্ভ করল, গ্রাম থেকে দলে-দলে পরিবার শহরে অনিশ্চিত জীবনধারায় বসবাস করতে আরম্ভ করল,তখন পল ভেরলেনের মতন কবিরা কবিতায় অনিশ্চয়তার ও অনির্ণেয়তার প্রয়োজন অনুভব করলেন । পল ভেরলেনের ‘আর্ট পোয়েটিক’ কবিতাটি বাস্তব জীবনে অনিশ্চয়তার উপস্হিতিকে কবিতায় আনতে চেয়েছে । তিনি অনুভব করলেন যে মানুষ চায় না তাকে সীমা দিয়ে বেঁধে রাখা হোক, সে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থাকতে চায় । নিজের বিবাহিত জীবন এবং পায়ুকামীদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ও কারাগারের জীবন থেকে তেমনটাই তাঁর মনে হয়ে থাকবে । ১৮৭৪ সালে যখন তিনি বললেন, ‘প্রথম এবং সর্বাগ্রে সঙ্গীত’, তখন ফরাসি কবিতায় নতুন কিছুর কথা বললেন তিনি । ফরাসি কবিতা চিরকালই সঙ্গীতময় ছিল, কিন্তু ভেরলেনের আগে কেউ বলেননি যে সঙ্গীতই কবিতায় মূল ব্যাপার । তার আগে তো ছিলই উপলবব্ধির গভীরতা, দৃষ্টিলব্ধ অবধারণা, বাচনিক নমনীয়তা ও পারিপাট্য । ভেরলেন সঙ্গীতকে কবিতায় গৌরবান্বিত করলেন । কবিতায় সঙ্গীত অদেখা বাস্তবতা সম্পর্কে যথাযথ হবার উপায় বাতলায় এবং যে বাস্তবতা স্পষ্টভাবে প্রভাবান্বিত করে তাকে কবিতার সিংহাসনে বসায় ।
চার
পল ভেরলেন আদেনেস থেকে জাঁ আর্তুর র্যাঁবো নামে সতেরো বছরের এক কবিযশোপ্রার্থীর চিঠি আর চিঠির সঙ্গে তার লেখা কয়েকটি কবিতা পড়ে মুগ্ধ হলেন, আর তাকে গাড়িভাড়া পাঠিয়ে বললেন প্যারিসে চলে আসতে । ১৮৭১ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর শার্লভিল থেকে প্যারিস পৌঁছোলেন র্যাঁবো, সঙ্গে নিজের পাণ্ডুলিপি নিয়ে, যার মধ্যে একটি কবিতার শিরোনাম ছিল, ‘দি ড্রাঙ্কেন বোট’ বা ‘মত্ত নৌকো’ । স্টেশনে কেউ ছিল না তাঁকে আপ্যায়ন করার জন্য। ভেরলেন, তাঁর বন্ধু শার্ল গ্রস্ত-এর সঙ্গে গার দু নর্দ আর গার্দ দ্যলেস্ত-এর মাঝে দৌড়ঝাঁপ করছিলেন তরুণ অতিথির জন্য । শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে মমার্ততে মাতিলদের বাবা-মায়ের বাড়ি ফেরার পথ ধরলেন ; পল ভেরলেন বিয়ের পর শশুরবাড়িতে থাকতেন । পথে তাঁরা খুঁজে পেলেন রোদে পোড়া গম্ভীর-মুখ, নীল চোখ, তরুণটিকে, যে, তাঁদের সঙ্গে আরদেনেসের বাচনভঙ্গীতে হ্যাঁ-হুঁ করে সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়ে কথা বলল ।
বারো বছর পরে তাঁর স্মৃতিচারণে ভেরলেন লিখেছেন যে, “তরুণটি ছিল দীর্ঘ, শক্ত কাঠামোর, খেলোয়াড়দের মতো আদরা, নিখুঁত ডিম্বাকার মুখ, যেন নির্বাসন থেকে ফেরা এক দেবদূত ; দেহের শক্ত কাঠামোর ওপরে শিশুসূলভ গালফোলা মুখ, হাবভাবে বয়ঃসন্ধি কাটিয়ে দ্রুত বেড়ে-ওঠা জবুথবুপনা ।” ভেরলেনের স্ত্রী আর শাশুড়ি তরুণটিকে বাড়িতে নিয়ে আসা যে ভালো হয়নি তা স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, কিন্তু তাড়াতে পারলেন না কেননা ভেরলেনের শশুর সেসময়ে বন্ধুদের সঙ্গে শিকারে গিয়েছিলেন । এক দিনেই তাঁরা টের পেলেন যে অতিথিটি চাষাড়ে, বাড়ির বাইরে বেরিয়ে উলঙ্গ হয়ে রোদ পোয়ায়, যে ঘরে থাকতে দেয়া হয়েছিল তাকে করে ফেলেছে নোংরা আর লণ্ডভণ্ড, যিশুর ছোটো ক্রস ভেঙে ফেলেছে, চুলে উকুন । ভেরলেন যা করতে চাইতেন অথচ করার সাহস পেতেন না, অতিথিকে সেসব করতে দেখে পুলক বোধ করছিলেন ।
অতিথিকে বন্ধুদের আড্ডায় নিয়ে গেলেন ভেরলেন । লিয়ঁ ভালাদে নামে ভেরলেনের এক বন্ধু তাঁর আরেক বন্ধুকে লিখে জানিয়েছিলেন, “তুমি পল ভেরলেনের নতুন আবিষ্কারের সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ পেলে না, ভেরলেন যে তরুণটির জন দ্য ব্যাপটিস্ট ; বড়ো-বড়ো হাতের চেটো, বড়ো-বড়ো পা, মুখ যেন তেরো বছরের বাচ্চার, চোখ দুটো নীল, আর তরুণটি ভিতু মনে হলেও, মতামত অসামাজিক মনে হলো, কল্পনাশক্তি অজানা কুকর্মে ঠাশা, বন্ধুরা তো সবাই তাকে দেখে একই সঙ্গে মুগ্ধ আর আতঙ্কিত । তরুণটি যেন ডাক্তারদের মাঝে একজন শয়তান ।” প্রকাশক গঁকুরভাইদের একজন জানিয়েছেন যে ভেরলেনের অতিথির সঙ্গে হাত মিলিয়ে মনে হচ্ছিল সবচেয়ে বজ্জাত কোনো খুনির হাত ।
মাতিলদের বাবার ফেরার আগের দিন ভেরলেনের অতিথিকে নিজের বাড়িতে কয়েকদিন রাখলেন শার্ল ক্রস ; তারপর পারনাসিয় কবি থিয়োদোর দ্যবাঁভিলের বাড়িতে চাকরানির ঘরে স্হান পেলেন । প্রথম রাতে জানলা দিয়ে নিজের ভিজে জামা-কাপড় রাস্তায় ছুঁড়ে-ছুঁড়ে ফেললেন তরুণটি, চিনামাটির বাসন ভেঙে ফেললেন, বিছানায় কাদামাখা জুতো পরে শুলেন, আর গোপনে কয়েকটা আসবাব বেচে দিলেন । বাঁভিলও এক সপ্তাহ কাটতেই ভেরলেনকে বললেন নিজের অতিথিকে ফেরত নিয়ে যেতে । তরুণটির আচরণে একমাত্র ভেরলেনই আহ্লাদিত হচ্ছিলেন । মাতিলদেকে নিয়ে কবিতাগুলো লেখার পর ভেরলেন নতুন কবিতা লেখার সময় পাননি। তরুণটি তাঁকে ওসকাচ্ছিলেন অনভিজাতের মতো জীবন কাটাতে এবং মদে চুর হয়ে দ্রষ্টার মতো কবিতা লিখতে । তাছাড়া পল ভেরলেন পেয়ে গিয়েছিলেন তাঁর পায়ুকামের আদর্শ সঙ্গী, যাকে এক বন্ধুর বাড়ি থেকে আরেক বন্ধুর বাড়িতে রক্ষিতার মতন লুকিয়ে রাখতে হচ্ছিল। ভেরলেন তাঁর অভিজাত পোশাক ছেড়ে নামানো-টুপি আর গলায় মাফলার ধরেছিলেন, অতিথির জন্য টাকাকড়ি খরচ করছিলেন প্রচুর । তাঁদের পায়ুকামের সম্পর্ক যখন আর গোপন রইলো না তখন ভেরলেনের বন্ধুরা তাঁর পাশ থেকে সরে যেতে লাগলেন । দুজনে মিলে গুহ্যদ্বার নিয়ে একটা সনেট লিখলেন ( Sonnet du trou cul ), যার প্রথম আট লাইন ভেরলেনের এবং পরের ছয় লাইন র্যাঁবোর । কবিতাটা ফরাসি থেকে ইংরেজিতে অনেকে অনুবাদ করেছেন ; আমি পল শ্মিট-এর অনুবাদটা দিলুম এখানে :
Hidden and wrinkled like a budding violet
It breathes, gently worn out, in a tangled vine
(Still damp with love), on the soft incline
Of white buttocks to the rim of the pit.
Thin streams like rivers of milk ; innocent
Tears, shed beneath hot breath that drives them down
Across small clots of rich soil, reddish brown,
Where they lose themselves in the dark descent…
My mouth always dribbles with its coupling force;
My soul, jealous of the body's intercourse,
Makes it tearful, wild necessity.
Ecstatic olive branch, the flute one blows,
The tube where heavenly praline flows,
Promised Land in sticky femininity.
র্যাঁবোকে একই সঙ্গে চরস আর আবসাঁথ খাইয়ে ভেরলেন অতিথিকে পরিচয় করিয়ে দিলেন নতুন অভিজ্ঞতার সঙ্গে, যার অন্বেষণ করছিলেন তিনি, ‘ইন্দ্রিয়গুলোর অপরিমেয় ও নিয়মানুগ বিশৃঙ্খলা’ ঘটানোর জন্য । ২১ অক্টোবর ১৮৭১ ভেরলেনের ছেলের জন্ম হলো এবং সংবাদটিতে আনন্দিত হবার বদলে ক্রুদ্ধ হলেন তিনি । মাতিলদে জানিয়েছেন যে অক্টোবর ১৮৭১ থেকে জানুয়ারি ১৯৭২ পর্যন্ত ভেরলেন তাঁকে মারধর করতেন আর খুন করার হুমকি দিতেন, একদিন সত্যিই গলা টিপে ধরেছিলেন, হাতখরচ না পেয়ে । স্বামীর দুর্ব্যাবহার আর মা-বাবার কাছে লুকোতে পারলেন না মাতিলদে, কেননা মাতিলদের দেহে আঘাতের চিহ্ণ আর স্বামীর কথা জিগ্যেস করলেই তাঁর কান্না থেকে তাঁরা বুঝে গিয়েছিলেন জাঁ আর্তুর র্যাঁবো নামে চাষার ছেলেটা আসার পরে কি ঘটছে মেয়ের শোবার ঘরে । জামাইয়ের পায়ুকামের প্রতি আকর্ষণের খবরও তাঁদের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল । ডাক্তার ডেকে মাতিলদেকে পরীক্ষা করিয়ে মেয়ে আর মেয়ের ছেলেকে পাঠিয়ে দিলেন তাঁদের পারিবারিক বাড়ি পেরিজিউতে ।
স্ত্রী চলে যাবার পর ভেরলেন বিয়েটা বাঁচানোর চেষ্টায় র্যাঁবোকে বললেন বাড়ি ফিরে যেতে ; সবকিছু ঠাণ্ডা হয়ে গেলে দুজনে আবার একত্রিত হতে পারবেন । প্যারিসে আসার ছয় মাস পরে মার্চ ১৮৭২ সালে বাড়িমুখো হলেন র্যাঁবো ; তিনি জানতেন যে তাঁকে ছাড়া ভেরলেনের চলবে না । মাতিলদে ছেলেকে নিয়ে প্যারিসে ফিরলেন, তাঁর মনে হলো মিটমাট হয়ে গেছে, চাষার ছেলেটা বিদেয় হয়েছে । ভেরলেনও চাকরি খুঁজতে লাগলেন । কিন্তু গোপনে চিঠি লিখতে লাগলেন র্যাঁবোকে, জানতে চাইলেন কেমন করে কোথায় দুজনে মিলিত হবেন । পায়ুকামর নেশায় ভেরলেনের কবিতা থেকে মিনার্ভা আর ভিনাস বিদায় নিয়েছিলেন । র্যাঁবোর প্রভাবে ভেরলেন তাঁর অন্তরজগতে লুকিয়ে থাকা দানবটাকে বাইরে বের করে আনার সুযোগ পেয়ে গেলেন । ভেরলেনের দানবকে সহ্য করতে না পেরে ১৮৭২ সালে মেয়ের সঙ্গে আইনি বিবাহবিচ্ছেদের অনুমতি দিলেন মাতিলদের বাবা, তখনও ডিভোর্স প্রচলিত হয়নি । ১৮৮৪ সালে ডিভোর্স আইনসঙ্গত হলে মাতিলদের সঙ্গে ভেরলেনের ডিভোর্স হয় । মাতিলদে আবার বিয়ে করেছিলেন এবং একষট্টি বছর বয়সে মারা যান ।
১৮৭২ সালের সেপ্টেম্বরে ভেরলেন আর র্যাঁবো লণ্ডন পৌঁছোলেন ; সেইসময়ে লণ্ডন ও বিশেষ করে সোহো ছিল ফরাসি কমিউনের পলাতক সদস্যদের লুকোবার পক্ষে ভালো জায়গা । কমিউনের প্রতি ভেরলেনের আগ্রহ থাকলেও র্যাঁবোর ছিল না । ভেরলেনকে তাঁর বুর্জোয়া মানসিক গঠন থেকে মুক্তি দেবার জন্য র্যাঁবো তাঁকে উৎসাহিত করলেন মুসেত এবং লেকঁত দ্যলিজের কবিতা পড়তে, ফরাসি কবিতার বারো মাত্রার ঐতিহ্য এবং ব্যালাডের আট মাত্রা অনুসরণ না করে দশ মাত্রার কবিতা লিখতে । র্যাঁবো তাঁকে পরামর্শ দিলেন কবিতা থেকে মানবিক কাহিনি, বাস্তববাদী ছবি আর ভাবপ্রবণ প্রতিকৃতি বাদ দিতে । পল ভেরলেনের মতে র্যাঁবোর ভালো লেগেছিল লণ্ডন ; তিনি ভেরলেনকে বলেছিলেন যে লণ্ডনের তুলনায় প্যারিসকে শহরতলি মনে হয়, লণ্ডনে রয়েছে কয়লা-চালিত ফ্যাক্ট্রি, টেমস নদীর ধারে জাহাজের ডক এবং সর্বোপরি একটি সাম্রাজ্যের রমরমা। ভেরলেন সেসমস্ত ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন না, তিনি কেবল কচি-তরুণ র্যাঁবোর সঙ্গে দৈহিক মিলনেই বেশি আনন্দ পেতেন, লণ্ডনে তাঁদের যথেচ্ছাচারে বাধা দেবার কেউ ছিল না । র্যাঁবোর ‘নরকে এক ঋতু’ কবিতার ‘ফুলিশ ভার্জিন’ প্রসঙ্গ ভেরলেন সম্পর্কে । তাঁরা ডেরা নিয়েছিলেন কামডেনের গ্রেট কলেজ স্ট্রিটে ( এখন রয়াল কলেজ স্ট্রিট ); বাড়িটিতে একটা প্লেট লাগানো আছে যে তাঁরা দুজনে সেখানে ছিলেন । নিজেদের ‘উৎকট দম্পতি’ হিসাবে উল্লেখ করেছেন র্যাঁবো । লণ্ডন থেকে প্যারিসে এক বন্ধুকে ভেরলেন লিখেছিলেন যে, “আমি আর ফরাসি সংবাদপত্র পড়িনা ; পড়ে হবেই বা কি?” তাঁরা দুজনে ব্রিটিশ মিউজিয়ামের গ্রন্হাগারে যেতেন বটে কিন্তু পল ভেরলেন যেতেন শহরের শীত থেকে বাঁচার জন্য, যখন কিনা র্যাঁবো যেতেন বিনে পয়সায় কাগজ-কলম-কালি পাওয়া যেতো বলে। বইপত্র পড়তেন । লণ্ডনের বাইরে বেড়াতে যেতেন দুজনে, ভেরলেন হ্যাম্পস্টেড হিথের কথা লিখেছেন, গ্রামাঞ্চল দেখার জন্য । র্যাঁবোকে ছাড়তে না পারার কারণ হিসাবে ভেরলেন লিখেছেন যে, এক ধরণের মিষ্টতা ঝলকাতো ওর নিষ্ঠুর ফিকে-নীল চোখে আর লালচে ঠোঁটের কটু ইশারায় । ইতিমধ্যে র্যাঁবো তাঁর বিখ্যাত কবিতা ‘মত্ত নৌকো’র আঙ্গিক ছেড়ে নতুন ধরণের গদ্য-কবিতার দিকে ঝুঁকছিলেন, যার পরিচয় পাওয়া যাবে তাঁর ‘নরকে এক ঋতু’ আর ‘ইল্যুমিনেশান্স’-এর কবিতাগুলোতে ।
লণ্ডন তাঁদের দুজনকেই অবাক করেছিল, আহ্লাদিত করেছিল । ভেরলেন বিস্মিত হয়েছিলেন দিগন্ত পর্যন্ত চলে যাওয়া রেলপথ আর লোহার সেতু দেখে, আর পথে-পথে নির্দয়, বারফট্টাই-মারা জনগণকে দেখে । ভেরলেন লিখেছেন লণ্ডন ছিল অতিশালীন, কিন্তু অসচ্চরিত্র হবার সব রকমের সুযোগ ছিল অবারিত, আর প্রচুর খরচ সত্বেও, তাঁরা সদাসর্বদা থাকতেন এইল, জিন আর আবসাঁথে মাতাল । আবসাঁথের সবুজ পরী র্যাঁবোকে ডাক দিয়েছিল ‘স্বরবর্ণ’ নামের কবিতাটি লিখতে ।
স্বরবর্ণ
A কালো, E শাদা, I লাল, U সবুজ, O নীল : স্বরবর্ণ
কোনো দিন আমি তোমার জন্মাবার কান্না নিয়ে কথা বলবো,
A, মাছিদের উজ্বল কালো মখমল জ্যাকেট
যারা নিষ্ঠুর দুর্গন্ধের চারিধারে ভন ভন করে,
ছায়ার গভীর খাত : E, কুয়াশার, তাঁবুগুলোর অকপটতা,
গর্বিত হিমবাহের, শ্বেত রাজাদের বর্শা, সুগন্ধলতার শিহরণ :
I, ময়ূরপঙ্খীবর্ণ, রক্তাক্ত লালা, নিঃসঙ্গের হাসি
যার ঠোঁটে ক্রোধ কিংবা অনুশোচনায় মাতাল :
U, তরঙ্গ, ভাইরিডিয়ান সমুদ্রের দিব্য কম্পন,
চারণভূমির শান্তি, গবাদিপশুতে ভরা, হলরেখার শান্তি
কিমিতির চওড়া পড়ুয়া ভ্রুজোড়া দিয়ে বিরচিত :
O, চরম তূর্যনিনাদ, অদ্ভুত কর্কশ আওয়াজে ভরপুর,
জগত আর দেবদূতে রেখিত নৈঃশব্দ :
O, সমাপ্তি, মেয়েটির চোখের বেগুনি রশ্মি !
র্যাঁবো খ্রিসমাসের জন্য বাড়ি ফিরলেও ভেরলেন ফিরতেন না ;র্যাঁবোর সমস্যা ছিল মা সবসময় বলতেন একটা চাকরি খুঁজে জীবনে স্হির হতে । ভেরলেন পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন সংসারের বাঁধন থেকে, দায়িত্ব থেকে, এবং পাপবোধে ভুগে কাঁদতেন মাঝেমধ্যে ; তাঁর কাছে র্যাঁবো ছিলেন ‘দীপ্তিময় পাপ’ আর র্যাঁবোর কাছে ভেরলেন ছিল ‘ক্ষুদে প্রিয়তমা’ । ইংরেজি শব্দের তালিকা তৈরি করেছিলেন এবং লণ্ডনে চাকরি খুঁজতে আরম্ভ করেছিলেন ভেরলেন। ফ্রান্সের গোয়েন্দা প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে পল ভেরলেনের ওপর লক্ষ রাখা হচ্ছিল। তাঁর ভবিষ্যতের জীবনীকার এদমন্দ লেপেলেতিয়েকে ভেরলেন লিখেছিলেন যে, “আশা করছি কয়েক দিনের মধ্যেই একটা বড়ো সংস্হায় চাকরি পাবো, যেখানে প্রচুর রোজগার করা যাবে, ইতিমধ্যে আমি কয়েকটা আমেরিকান সংবাদপত্রের জন্য কাজ করছি যারা ভালো পয়সাকড়ি দ্যায় ।” লেপেলেতিয়ে তার কোনো প্রমাণ পাননি, এবং সবই ভেরলেনের বানানো, ফরাসি কবিদের ঈর্শ্বান্বিত করার জন্য । দুজন ভবঘুরে লণ্ডনের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন কাজের জন্য কিন্তু কারোর সাড়া তাঁরা পাননি । লেপেলেতিয়ে একটা কাগজের বিজ্ঞাপন জোগাড় করতে পেরেছিলেন, সম্ভবত র্যাঁবোর তৈরি খসড়া :
এক ফরাসি ভদ্রলোক ( ২৫ ), অভিজাত সমাজে যাঁর ভালো যোগাযোগ আছে, উচ্চশিক্ষিত, ফরাসি ডিপ্লোমাধারী, ইংরেজিতে সড়গড়, এবং বিপুল সাধারণ জ্ঞানের মানুষ, ব্যক্তিগত সচিব, পর্যটনের সঙ্গী কিংবা গৃহশিক্ষকের চাকরি খুঁজছেন । সম্ভ্রান্তদের সুপারিশ আছে । ঠিকানা : ২৫ ল্যানঘাম স্ট্রিট ।
র্যাঁবোর ‘ইল্যুমিনেশান্স’-এর ‘ভবঘুরে’ কবিতাটি ( ১৮ নং ইল্যুমিনেশান ) তাঁদের দুজনের সেই সময়টিকে ধরে রেখেছে :
সমব্যথী ভাই ! ওর কাছে আমার কোনও নৃশংস নিশিপালন আছে ! ‘আমি এই ঝুঁকিপূর্ণ কর্মপ্রচেষ্টাকে দখল করে নিতে বিফল হয়েছিলুম । আমি ওর অকর্মণ্যতা নিয়ে ঠাট্টা করেছিলুম । যদি আমাদের নির্বাসনে যেতে হয়, কেনা-গোলমী করতে হয়, তা হবে আমার দোষ।’ অদ্ভুত দুর্ভাগ্য আর বোকামির জন্য ও আমার প্রশংসা করেছিল, আর তার সঙ্গে জুড়েছিল অশান্তিকর কারণ ।
এই শয়তান পণ্ডিতকে আমি বিদ্রুপ করে উত্তর দিয়েছি, আর জানালার কাছে গিয়ে তা শেষ করেছি । বিরল সঙ্গীতরেখার চালচলনের অপর পারের চারণভূমিতে আমি ভবিষ্যতের রাতের বিলাসের মায়াপুরুষ গড়েছি ।
এই অস্পষ্ট স্বাস্হবিধিসন্মত চিত্তবিক্ষেপের পর, আমি খড়ের মাদুরের ওপরে হাতপা ছড়িয়ে শুয়ে পড়তুম । এবং, বলতে গেলে প্রতি রাতে, যেই আমি ঘুমিয়ে পড়তুম, বেচারা ভাইটি উঠে পড়তো, মুখে দুর্গন্ধ, চোখে দেখতে পাচ্ছে না -- যেমন ও নিজের সম্পর্কে স্বপ্ন দেখতো -- আর নিজের নির্বোধ কান্নার স্বপ্নে বিভোর আমাকে ঘরের ভেতরে টানাটানি করতো !
বাস্তবিক, সত্যি বলতে কি, আমি ওকে ওর সূর্যসন্তানের প্রাগৈতিহাসিক স্হতিতে ফিরিয়ে আনার প্রতিজ্ঞা করেছিলুম -- আর আমরা ঘুরে বেড়ালুম, গুহার মদে ভরণপোষণ করে, আর পথের বিসকিট খেয়ে, আমি পরিসর আর ফরমুলা খুঁজে পাবার জন্যে অধৈর্য ।
তাঁদের দুজনের ঝগড়া গ্রেট কলেজ স্ট্রিটেই আরম্ভ হয়েছিল । তাঁদের সম্পর্ক তিক্ত হয়ে উঠেছিল । র্যাঁবো মাঝে একদিন ছুরি দিয়ে ভেরলেনের উরুতে আঘাত করেছিলেন । প্রেমিকের আঘাতের আদর বলে মেনে নিয়ে কাউকে জানাননি ভেরলেন । এই বিষয়ে ভেরলেন লিখেছেন, “আমি বাড়ি ফেরার সময়ে দেখলুম জানলা দিয়ে র্যাঁবো আমায় দেখছে । অকারেণেও আমাকে দেখে অপমানজনক ঠাট্টা-ইয়ার্কি করতে লাগলো। যাহোক আমি সিঁড়ি দিয়ে উঠলুম আর ঘরে ঢুকলুম । ‘তোমার কি কোনো ধারণা আছে এক হাতে একবোতল তেল আর অন্য হাতে একটা মাছ ঝুলিয়ে কেমন দেখাচ্ছিল তোমায় ?’ বলল র্যাঁবো । আমি তার জবাবে বললুম, আমি তোমাকে জোর দিয়ে বলতে পারি, আমাকে মোটেই উপহাসাস্পদ দেখায়নি ।’ ভেরলেন মাছটা দিয়ে র্যাঁবোর মুখে সপাটে মারলেন আর জানালেন যে তিনি আত্মহত্যা করে নেবেন । ভেরলেন চটে গিয়ে জাহাজ ধরে সোজা চলে গেলেন বেলজিয়াম, স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক জোড়া লাগাবার উদ্দেশে । সেখানে মাতিলদে ছিলেন ।
র্যাঁবো কিছুক্ষণ পরেই ডকে পৌঁছে টের পেলেন যে ভেরলেন, তাঁর ‘বুড়ি শূকরী’ , সত্যিই চলে গেছেন । নিষ্কপর্দক র্যাঁবোকে সাহায্য করার কেউ ছিল না, আর যারা ছিল তারা দুজনের দৈহিক সম্পর্ক জানতে পেরে নিজেদের দূরে সরিয়ে নিয়েছিল । র্যাঁবো ভেরলেনকে চিঠি দিলেন :
তুমি কি মনে করো যে আমার বদলে অন্য লোকেদের সঙ্গে থাকলে তুমি আনন্দে থাকবে ? ভেবে দ্যাখো ! নিশ্চয়ই না ! আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে ভবিষ্যতে আমি তোমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করব । আমি তোমাকে অত্যন্ত ভালোবাসি, আর তুমি যদি ফিরতে না চাও, কিংবা আমি তোমার কাছে যাই তা না চাও, তুমি একটা অপরাধ করছ, আর তার জন্য তুমি সমস্ত স্বাধীনতা হারিয়ে বহুকাল আফশোষ করবে, আর এতো ভয়ঙ্কর দুঃখদুর্দশায় ভুগবে যার অভিজ্ঞতা তোমার কখনও হয়নি ।
১৮৭৩ সালের ৮ জুলাই র্যাঁবোকে টেলিগ্রাম করলেন ভেরলেন ব্রুসেলসের হোটেল লিজে পৌঁছোতে । ভেরলেনের জামাকাপড় বেচে র্যাঁবো পৌঁছোলেন বেলজিয়ামের হোটেলে যেখানে ভেরলেন ছিলেন । দুজনের মনের মিল হল না, টানা কথা কাটাকাটি চলল । ভেরলেন একের পর এক আবসাঁথের বোতল খালি করে মাতাল হয়ে থাকতে চাইলেন । ১০ জুলাই তিনি একটা রিভলভার আর গুলি কিনলেন, আত্মহত্যা করবেন ভেবে । চারটে নাগাদ মাতাল অবস্হায় দুটো গুলি চালালেন র্যাঁবোকে লক্ষ করে । একটা গুলি লক্ষভ্রষ্ট হল, অন্যটা লাগল র্যাঁবোর কনুইতে । আঘাতকে বিশেষ গুরুত্ব না দিয়ে সঁ-জাঁ হাসপাতালে ড্রেসিং করিয়ে ব্রুসেলস ছাড়ার কথা ভাবলেন র্যাঁবো । সন্ধ্যা আটটা নাগাদ র্যাঁবোকে গারে দু মিদি রেলস্টেশনে ছেড়ে দেবার জন্য ভেরলেন আর ভেরলেনের মা গেলেন । আদালতে র্যাঁবোর সাক্ষ্য অনুযায়ী ভেরলেন পাগলের মতো আচরণ করছিলেন আর তাঁর পকেটে পিস্তলও ছিল । র্যাঁবো পুলিশের একজন টহলদারকে দেখতে পেয়ে দৌড়ে তার কাছে গিয়ে বললেন তাঁকে ভেরলেনের থেকে বাঁচাতে । ভেরলেন গ্রেপ্তার হলেন, তাঁর বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টার অভিযোগ উঠল, আদালতে তাঁদের দুজনের সম্পর্ক নিয়ে উকিল আর ডাক্তারদের প্রশ্নের মুখে পড়লেন ভেরলেন ।
১৭ জুলাই র্যাঁবোর বুলেট বের করার পর তিনি নালিশ তুলে নিলেন । পুলিশকে দেয়া বয়ানে র্যাঁবো লিখেছিলেন যে, গুলি চালিয়েই ভেরলেন তাঁর অপরাধের জন্য তক্ষুনি ক্ষমা চেয়ে নিলেন । পিস্তলটা আমার হাতে দিয়ে বললেন তাঁর কপাল লক্ষ করে গুলি চালাতে। তাঁর আচরণ ছিল গভীর অনুতাপের । ভেরলেনের বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টার অভিযোগ তুলে নিয়ে কেবল আঘাত করার অভিযোগ বজায় রইলো । তাঁদের পরস্পরের পায়ুকাম নিয়ে আদালতে অপমানজনক কথাবার্তা হলেও তাকে অপরাধ বলে মনে করা হয়নি এবং পুলিশ আরোপ করেনি । ৮ই আগস্ট ১৮৭৩ ভেরলেনের দুই বছরের কারাদণ্ডের আদেশ হল ।
র্যাঁবো শার্লভিল ফিরে গিয়ে ‘নরকে এক ঋতু’ লেখা শেষ করলেন । তাতে ভেরলেনকে তিনি ‘উন্মাদিনী ভার্জিন’ হিসাবে উল্লেখ করেছেন, আর নিজেকে ‘নারকীয় স্বামী’ হিসাবে আর তাঁদের একসঙ্গে বসবাসকে বলেছেন ‘গার্হস্হ প্রহসন’। ১৮৭৪ সালে র্যাঁবো ফিরেছিলেন লণ্ডনে, কবি জারমেইন নোভোর সঙ্গে, তিন মাস ছিলেন একসঙ্গে । এই সময়ে তিনি ‘ইল্যুমিনেশান্স’-এর গদ্য-কবিতাগুলো লেখা শেষ করেন । কিন্তু পায়ুকামের নায়ক-নায়িকা বা আদম-ইভের কাহিনি এখানেই ফুরোয়নি । জেল থেকে র্যাঁবোকে চিঠি লিখতেন আর নিজের নতুন লেখা কবিতা পাঠাতেন, যেগুলো পড়ে র্যাঁবো মোটেই উৎসাহিত হতেন না । র্যাঁবো তখন কবিতা ও সাহিত্যজগত সম্পর্কে উদাসীন এবং নতুন জীবনের সন্ধান করেছেন, বাবার মতো উধাও হয়ে যেতে চাইছেন । পরস্পরের দৈহিক ভালোবাসার বদলে যিশুখ্রিস্টকে ভালোবাসার কথা বলছেন তখন ভেরলেন । র্যাঁবো ঠাট্টা করে তাঁকে লিখলেন যে ‘লয়োলা’ স্টুটগার্টে এলে দেখা হবে । লয়োলা ছিলেন এক যিশুভক্ত পাদ্রি ।
পরস্পরের সাক্ষাতের সেই মুহূর্তটা এলো এবং কমেডি ছাপিয়ে গেল ট্যাজেডিকে । ভেরলেন গোঁ ধরলেন র্যাঁবোকে দীক্ষিত করার জন্য, একটা শুঁড়িখানায় দুজনে একত্রিত হয়ে । ভেরলেন আর র্যাঁবো দুজনেই মাত্রাহীন মদ টেনে মাতাল হলেন এবং আবার কথা কাটাকাটি আরম্ভ হল । শুঁড়িখানা থেকে বেরিয়ে দুই বিখ্যাত কবির মধ্যে হাতাহাতি মারামারি আরম্ভ হল। র্যাঁবোর সঙ্গে পেরে ওঠা অসম্ভব ছিল ভেরলেনের পক্ষে । মার খেয়ে মাতাল ভেরলেন, রক্তাক্ত, পড়ে রইলেন পথের ধারে ।
সাত এম-এম ছয়গুলির পিস্তলটা ক্রিস্টির নিলামে কেউ ষাট হাজার ডলারে সম্প্রতি কিনে নিয়েছেন ; তার আগে পিস্তলটা ছয়বার নিলাম হয়েছিল । মায়ের দেয়া টাকায় ‘নরকে এক ঋতু’ ছাপিয়ে, মাকে এক কপি দিয়ে, কবিতার প্রতি র্যাঁবোর আকর্ষণ শেষ হয়ে গিয়েছিল ; ইল্যুমিনেশান্স’ আর ছাপাবার প্রয়োজন বোধ করেননি, যা করার কোরো বলে পাণ্ডুলিপি ভেরলেনকে দিয়ে পাড়ি দিয়েছিলেন আফ্রিকায়, ভিন্ন জীবনের সন্ধানে । ভেরলেন কবিতাগুলো মে-জুন ১৮৮৬-এ ‘প্যারিস লিটেরারি রিভিউতে’ প্রথমে প্রকাশ করার জন্য দেন । তারপর গ্রন্হাকারে প্রকাশের ব্যবস্হা করেন ১৮৮৬ সালের অক্টোবরে ।
-------------------------------------------------------------XXXXXXXXXXX-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 বহতা অংশুমালী মুখোপাধ্যায় | 27.58.255.50 | ১১ আগস্ট ২০২১ ১৮:৩১734861
বহতা অংশুমালী মুখোপাধ্যায় | 27.58.255.50 | ১১ আগস্ট ২০২১ ১৮:৩১734861মলয় রায়চৌধুরীর ডিটেকটিভ উপন্যাস ‘অলৌকিক প্রেম ও নৃশংস হত্যার রহস্যোপন্যাস বা নোংরা পরির কংকাল প্রেমিক’-এর আলোচনা
বহতা অংশুমালী মুখোপাধ্যায়
উপন্যাস এর নামটা আমাকে বুঝতেই দেয় নি ভিতরের খনিজের উপস্থিতি । প্রচ্ছদে যুবতীর ছবি দেখে মনে হয় কোনো রগরগে রবিবাসরীয়ের সামনে দাঁড়িয়ে পড়েছি। বুঝি নি এই অতি সংক্ষিপ্ত উপন্যাসের প্রতিটি লাইন এক বিরল জীবনদর্শনের মুখোমুখি করে দেবে আমাকে । এক অন্যধরণের সত্যানুসন্ধান , সাধারণ খুনের মামলার প্রেক্ষাপটে যা এক যুবক যুবতীর উৎকেন্দ্রিক আরণ্যক ভালোবাসা থেকে শুরু হয়ে শেষ হয় পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে। তেলেগুতে এনক্রিপ্টেড, বাংলায় লেখা , সিডিতে সংরক্ষিত ডায়রিলেখনে বন্দী হয়ে থাকে সেই জীবনকাহিনী । আর কংকাল প্রেমিক এর জীবন ও মৃত্যু রহস্য উন্মোচিত হয় নোংরা পরীর হাতে।
নোংরা পরী , ববিটাইজিং ভীতির কার্যকারিতা আর সারল্যের সংজ্ঞা
নোংরা পরী বেরিয়ে এসেছে Edith Wharton এর বর্ণিত The Age of Innocence এর পর্দা কেটে । ইন্সপেক্টর রিমা খান অপরাধীর চোখের গতির ভিত্তিতে ক্রিমিনাল ঠ্যাঙায় । যে ক্রিমিনালরা জেরা করার সময়ে পায়ের দিকে তাকিয়ে থাকে তাদের দু-ডিগ্রি , যারা মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে তাদের থার্ড ডিগ্রি । বুকের দিকে তাকিয়ে থাকারা নাকি তুলনামূলক ভাবে স্বাভাবিক, রিমা খানের ভাষায় তারা প্রকৃতির মাদার-সান-ইন্সটিংক্ট মেনে চলে। তাদের ঠেঙিয়ে কথা আদায় করে না , সাবইন্সপেক্টারের ওপর ছেড়ে দেয় ।
রিমা খানকে উপন্যাসের পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নাম দিয়েছে "নোংরা পরি" । নোংরা- কারণ সে সিমেন-দি-বভার সেকেণ্ড-সেক্স হতে রাজী নয়। সে আদ্যোপান্ত পুলিশ , প্রফেশনাল সমস্ত অর্থে , এমনকি ছুটকো ঘুষ নেবার ক্ষেত্রেও । সে দুর্দান্ত , দুঁদে । তার ভয়ে তার অঞ্চলের ক্রিমিনালরা লোক্যালিটি বদলে ফেলে ।
বেটি ফ্রিড্যান যে ফেমিনিন-মিস্টিক কে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন তা এখনো আজকের সমাজেও পৃথিবী জুড়ে বর্তমান । এই নারীত্বের রহস্য শতকের পর শতক কখনো চীনে মেয়েদের পা জুতোয় ঢুকিয়ে ছোটো করতে বাধ্য করে , আফ্রিকার উপজাতির মেয়েদের মরাল গ্রীবাকে দীর্ঘায়িত করতে ধাতব বালায় বালায় বরবাদ করে দেয় ঘাড়ের মাথাকে ধরে রাখার কার্যকারীতাটুকু। এই নারীত্বের সন্ধানে ইউরোপের শিক্ষিতা মহিলা প্রেমপত্রে বানান ভুল করে, পদার্থবিদ্যার ডিগ্রি না নিয়ে পড়তে চায় সুললিত আর্টস।
রিমা খানের মধ্যে সেই সারল্যটুকু নেই , সভ্যতা যে সারল্য শেখায় মেয়েদের, কাঁচের-পাথরবাটির মতো । যে শিক্ষিত সারল্যে মেয়েরা দুই বাচ্চার মা হয়ে গিয়েও সেক্সটকের অধিকার পায় না, বলে "ইস ছি ছি ছি", আজকের জমানাতেও । রিমা খান বিন্দাস গালিগালাজ করে। রিমা আবিষ্কার করে ফেলেছে যে ববিটাইজ করার ভয় দেখালে আবালবৃদ্ধ-ক্রিমিনাল খুব আকুল হয়ে পড়ে । তাতে অরগ্যাজম হয় রিমা খানের । এখন যে যুগ এ জিন্স এর সঙ্গে এক-হাত লাঠি-চুড়ি পরে মডার্ন ফেমিনিন ঘুরে বেড়ায় , স্ট্রিপটিজ দেখে আবার সন্তোষীমা-ও করে , সেখানে এই ডিলডো প্রেমী পুলিস অফিসারটি নোংরাও বটে পরীও বটে। তাকে কোথাও প্লেস করা যায় না, কোনো গ্রাফ এ ফেলা যায় না ! তার উলঙ্গ সত্ত্বায় কোনো কালো-দস্তানা-মোজা পরা লজ্জার ভেজাল ভঙ্গিমাও নেই । তাই সে মানুষী নয়। মানুষের ভোগ্যাও নয় হয়তো । বাঘিনী বাঘের জন্যে ভার্জিনিটি-টুকু বাঁচিয়ে রেখে ছিল । তা চারদিকে তো শুধুই ছাগল গবাদি পশু তার । তাই কুমারীত্ব ঘোচেনি কোনোদিন । এক ব্যতিক্রম কংকাল প্রেমিক ।
যে কংকাল সে শুধু প্রেমিক
প্রেম কয়প্রকারের হয়ে থাকে ? বহু প্রকারের হয়ে থাকে প্রেম। মেয়ে মাকড়শার সামনে পুরুষ মাকড়শার সুইসাইডাল প্রেম, মক্ষীরাণীর সামনে খুদে মৌমাছি শ্রমিকের প্রেম , রেপিস্ট হাঁসের প্রতি হংসিনীর প্রেম, ডলফিনের হরণ বা অপহরণ মূলক প্রেম , সতী নারীর পতিপ্রেম , বড়োলোকের বেশ্যাপ্রেম এবং সমান্তরাল ভাবে সন্তানের মায়ের প্রতি প্রেম এমন অনেক রকমের ।
আমাদের কংকাল , যিনি কিনা ইন্সপেক্টর রিমা খানের আবার চাকরি ফিরে পাবার পাসপোর্ট, তিনি ছিলেন গণিতবিদ । এখানে মলয় রায়চৌধুরী বোধ হয় গণিতের অবতারণা করেছেন কুয়াসাহীন শুদ্ধচিন্তার প্রতীক হিসেবে। নিরঞ্জন, ওরফে কঙ্কাল , বুঝে গিয়েছিলেন তিনি বহুগামী । তাই কোন মহিলাকে এবং নিজেকে সমস্যা না দিতে চেয়ে , বিয়ে টিয়ে না করে , শুদ্ধ গণিত ও শুদ্ধ যৌনতার চর্চা করেছেন প্রেমে পড়ার আগে অব্দি। মলয় রায়চৌধুরী দেখিয়েছেন তাঁর দুরকম প্রেম ।
নিম্নগামী প্রেমটি (মস্তিষ্ক থেকে শীষ্ণ হয়ে এসে হৃদয়ে যা ইকুইলিব্রিয়াম পেলো , মাসিকের আবর্তনে মাপলো সময় )
একজন জীবন খুঁজতে পালিয়েছিল , অন্যজন গিয়েছিল শুধু পলায়নপরাকে দেখে । মায়া পাল পুরোদস্তুর আধুনিক যুবতী , যিনি কুড়ুমুড়ে ইংরেজী বলতে বলতে অনায়াসে উচ্চপদের চাকরি পেতে পারেন , তিনি সুপুরুষ গণিতবিদের হাত ধরে বললেন "চলুন পালাই" । আর কামুক বিশ্বামিত্র ও তাঁর সঙ্গিনী চললেন অরূপের সন্ধানে, অন্ধ্রপ্রদেশের ব্যারাইটস খনি অঞ্চলে । তাঁদের অতিপ্রাকৃত ও অতিপ্রাকৃতিক প্রেম সেই অরণ্যে যাপিত হয়। অতিপ্রাকৃতিক কারণ মলয় রায়চৌধুরী এখানে খুঁজতে চেয়েছেন প্রকৃতির সঙ্গে মিথোজীবী ভাবে যাপিত জীবনের দিকটি । বাছুরকে দুধ থেকে বঞ্চিত না করে, মুরগীর ছাল ছাড়িয়ে না নিয়ে, ভেড়ার লোম কেটে না নিয়ে বাঁচার পদ্ধতি । মায়ার এনভায়রনমেণ্টালিজম, জীবপ্রেম ।
মলয় রায়চৌধুরী এখানে মনে করিয়ে দেন আমাদের ভুলে যাওয়া নারী পুরুষের প্রেমের রূপটিও । এখানে এক মানুষীর গায়ের গন্ধটি প্রেমিক চেনেন । প্রেমিক প্রেমিকাকে আলিঙ্গন করতে থাকেন মনের তাপে, আর রোজ আলিঙ্গন করতে করতে বুঝতে পারেন তাপের তারতম্য , ডিম্বাণুর আবির্ভাব। তাঁরা প্রেমটুকু চেয়েছিলেন , বীজটুকু নয়। তাই নিরোধ প্রক্রিয়া , অদ্ভুত আত্মনিয়ন্ত্রণ । মায়া নিরঞ্জনকে সেই প্রেম শেখান যাতে শরীর বড় হয়েও ওঠে না অযথা , ছোটও হয় না। যতটুকু আসে সহজে আসে। এই প্রথম নিরঞ্জন কোনো নারীর আলিঙ্গনে উত্তেজিত না হয়ে শান্ত হন।
এখানে খুব সুন্দর ভাবে দেখানো হয়েছে দুজন মানুষের একে অন্যকে কেন্দ্র করে বেঁচে থাকার আনন্দ। এখানে নিরঞ্জন ঘড়ির অভাবে মায়ার মাসিক বা ঋতূস্রাব এর দিন গুলিকে গাছের গুঁড়িতে খোদাই করে রাখেন । আর হিসেব রাখেন দিন মাস বছরের । "Metaformic theorists also discuss how cultures, like the Romans and Gaelic used the same words for menstruation and the keeping of time, while the Mayan calendar was directly influenced by women's menstrual cycles."(উইকিপিডিয়া থেকে উদ্ধৃত) উইকিপিডিয়া আর গুগল আমাদের বলে দেবে , মহাজাগতিক ক্যালেণ্ডারটি অনেক ক্ষেত্রেই কিভাবে প্রাচীন কালে নারীর শরীরের ঋতূচক্রের দিকে তাকিয়ে বানানো হয়েছিল । কখনো উনত্রিশ কখনো ত্রিশ দিনের বিরতিতে।
এই প্রেমে এক মানুষী বলেন আমি সবটুকু দেব, আর পুরুষটি বলেন আমি সবটুকু নেব । আর ঋতূস্রাবের পরে প্রেমিক ধুইয়ে দেন পরম আদরে প্রেমিকার রসস্থল , আরণ্যক দিনে ।
ঊর্ধ্বগামী ভালোবাসা (সখীর জন্যে বীজ শুয়ে আছে বরফে)
শরীরের ভালোবাসাকে আমরা মাঝে মাঝেই একটু নিম্নমানের বলি, পর্দা তুলে দিই । "রজকিনী প্রেম নিকষিত হেম, কামগন্ধ নাহি তায়" । যেন কামগন্ধ খারাপ বস্তু । যেন আমাদের সব্বার উৎস্য লজ্জার । এই ক্রিশ্চান ওরিজিন্যাল-সিন এর পাপবোধ যা আমাদের উপরে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে , যে পাপবোধ থেকে আজ বহু মেয়ের অঙ্গ কেটে দেওয়া হয় যাতে তারা "শয়তানি আনন্দ" উপভোগ না করে শুধু সন্তান প্রসবের যন্ত্র হিসেবে নিজেদের বহন করতে পারে, সেখানে মিলি একদমকা খোলা হাওয়া । মিলি কিশোর আনাড়ি নিরঞ্জন কে "ভালোবাসতে" শেখায় । তারা বিভিন্ন পদ্ধতিতে নিজেদের শরীর নিয়ে খেলে , জানতে পারে যান্ত্রিক ভঙ্গীতেই বিভিন্ন আনন্দের উৎস্যমুখ । সে তো সেতার বাজাবার আগে টুংটাং টুকু না করলেই নয়।
মিলি ভালোবেসেছিল কংকালকে। নিরঞ্জন ভালোবাসেননি সেই অর্থে। তিনি তখন-ও পুরুষ নন। বৃন্দাবনবিলাসী কিশোর , যে পালিয়ে যাবে , পালিয়ে গেছে। কিন্তু মিলি বিয়ে করেন নি । আর নিরঞ্জনের সন্তান পাওয়ার জন্যে জোরাজুরিও করেছেন বহু বছর পরে দেখা হলে ।
নিরঞ্জন ভালোবেসেছেন মায়াকে । কিন্তু মিলির জন্যে মৃত্যুর আগে রেখে গেছিলেন শুক্র, ডাক্তারের কাছে ।
মিলি সন্তান চেয়েছিল, মায়া চায়নি । এখানে শিষ্ণ থেকে উঠে গেছে ভালোবাসা হার্ট এ । কি মন্ত্রে কে জানে।
এক্ষেত্রে মলয় রায়চৌধুরীর একটি ইণ্টারভিউ মনে পড়ে গেল Alexander Jorgensen কে দেওয়া। " Alex: If you could walk a mile in whatever circumstance, where would you choose to do it ?
Malay : I would go to the bank of river Ganges, at the place where I had kissed my Nepali classmate Bhuvanmohini Rana. My first and memorable kiss. I do not know where she is now. Must have become old or might have died ; she was two years older than me. I would sit at the same spot at the same time of autumn evening to revisit her tenderness." । আমার যেন মনে হয় ভুবনমোহিনী কোথাও মিলি , তার সমস্ত কোমলতা নিয়ে, যেখানে নিরঞ্জনের কৈশোর আটকে আছে।
মায়ার সত্যি নিরঞ্জনের সত্যি , মায়ার জীবনদর্শন
কাহিনীটি তো ডিটেকটিভকে নিয়ে। সত্যানুসন্ধান ! Akira Kurosawa র Rashomon যেমন দেখিয়ে দেয়, বিষয়গত তথ্য আর বিষয়ীগত সত্য এক নয় , প্রেমিক নিরঞ্জন ও প্রেমিকা মায়ার সত্যিও আলাদা।
মায়া আধুনিক , কিন্তু পুনরাধুনিক। তিনি জানতে চেয়েছেন জীবনের যাপনগত সত্যটা । মানুষ ঠিক কোন আঙ্গিকে সভ্য , জীবহত্যার ঊর্ধ্বে উঠে প্রকৃতির সঙ্গে মিথোজীবীতার মাধ্যমে বাঁচা যায় কিনা, তাই দেখতে চেয়েছিলেন তিনি। তাই দুধের শিশুকে ছেড়ে, স্বামীর ও সমাজের দেওয়া অসহিষ্ণুতা ও অপমান থেকে পালিয়ে যেতে , তিনি "খপ করে" নিরঞ্জনএর হাত ধরে বলেছিলেন "চলুন পালাই " ।
“No, it is impossible; it is impossible to convey the life-sensation of any given epoch of one’s existence--that which makes its truth, its meaning--its subtle and penetrating essence. It is impossible. We live, as we dream--alone.” -- Joseph Conrad এই জাতীয় উক্তি কে মেনে নিতে পারেননি ইংরাজির ছাত্রী মায়া পাল। নিরঞ্জন লিখেছেন , "সে আমাকে টমাস হবস, জোসেফ কনরাড, অ্যান্টনি বারজেস, উইলিয়াম গোলডিং আরো কারা কারা যেন, প্রতিটি নাম মনেও নেই এতদিন পর , এনাদের লেখালিখির কথা শোনাতো । তার জীবনের অতীতসূত্র কেবল এই সাহিত্যদর্শনকে ঘৃণা । তার অতীত সম্পর্কে আর বিশেষ কিছু জানি না, সে বলতে চায়নি । বলত ওনারা জীবনের ভুল ব্যাখ্যা করে গেছেন । ওনারা নাকি বলে গেছেন একজন মানুষের জীবন সংক্ষিপ্ত, সে একাকী, কেউ নেই তার, যত বৈভব থাক না কেন সে প্রকৃতপক্ষে দরিদ্র , পঙ্কিল, কদর্য, অশ্লীল, জঘন্য, স্হূল, পাশবিক, অশিষ্ট ও বর্বর । সে বলত, জীবনের এই আশাহীন দৃষ্টিকোণ অসত্য । "
কিন্তু নিরঞ্জন এর সত্য আলাদা। তিনি মূলতঃ প্রেমিক । তিনি নিজেকে দেখেন এইভাবে -"মায়ার পাশে বসে একই ভাবনা ঘুরছিল আমার মগজে, যা বহুকাল থেকে বাসা বেঁধে আছে । তা এই যে, আমি একজন কুকুর । যে মালকিনির হাতে পড়েছি, সে যেরকম চেয়েছে, যেরকম গড়েছে, তা-ই হয়েছি : প্রেমের কুকুর, কাজের কুকুর, সেবার কুকুর, গুপ্তচর কুকুর, ধাঙড় কুকুর, কুরিয়ার কুকুর, প্রেডাটার কুকুর , পাহারাদার কুকুর, মানসিক থেরাপির কুকুর, অনধের কুকুর, শোনার কুকুর, শোঁকার কুকুর, চাটার কুকুর, রক্ষক কুকুর, গাড়িটানার কুকুর, আদরের কুকুর, এই কুকুর, ওই কুকুর ইত্যাদি । কিন্তু আমার লেজটা জন্মের সময়ে যেমন আকাশমুখো ছিল, আজও তেমনই আছে । থাকবে । এখন টাইপ করতে বসেও জানি, লেজটা অমনই রয়েছে ।" এই আকাশমুখী লেজ এই গণিতবিদের জীবনচেতনা ।
নিরঞ্জনের জীবনচেতনার অন্য একটি দিক দেখা যায় , তাঁর চেতনায় "পবিত্র" শব্দটির অভিঘাতে । নিরঞ্জন লিখছেন - "আমার দিকে না তাকিয়েই মায়া বলেছিল, আমরা সারা জীবন নিজেদের সম্পর্ক আপনি-আজ্ঞের পবিত্র গভীরতায় রাখব । তুমি-তুমি ওগো-হ্যাঁগোর ছেঁদো নোংরা রুটিনে বাঁধা পড়ব না। বলেছিলুম, পবিত্র ? এই ধরণের অস্পষ্ট শব্দ ব্যবহার করবেন না প্লিজ । "
নিরঞ্জন এক জমির মতন পড়ে থাকেন সমস্ত জীবন । নানান মেয়ে , মহিলা তাঁর উপর দিয়ে বয়ে যান , তাঁকে উর্বর করেন , তাঁকে ভেঙ্গে দেন । তাঁর ল্যাণ্ডস্কেপ পালটে দেন। এভাবেই মানবজমিনের চাষ করে গেছেন নিরঞ্জন । শেষ দিন অবধি। তিনি কোনো মহিলা কে "ডিমিন" করেন নি কখনো । দেহ ব্যবসায়িনীর "গিগলিং" টুকুকেও নয়। "পৃথিবী নামের ছোট্টো দ্বীপটায়, নারী ছাড়া আমি একা, নিঃসঙ্গ, অন্তরীণ । জীবনে নারী নেই ভাবলেই মনে হয় মরে যাবো, মরে যাচ্ছি, মরে গেছি ; ফাঁকা, ফোঁপরা, খালি । জানতেই পারতুম না আহ্লাদ কি, আঘাত কি, বেদনা কি, হাহাকার কি । " - নিরঞ্জন এমনই ভাবেন, বলেন , বাঁচেন। এই নারীসঙ্গ ইচ্ছা সামগ্রিক শারীরীক কাম নয় একেবারে। তিনি শেষ বয়সেও ‘শেষনীর’ সঙ্গ চান উত্থানরহিত অবস্থায় । যেমন "অ্যালিস ইন দ্য ওয়াণ্ডার ল্যাণ্ড" এর লেখক লুই ক্যারল এর স্নেহের ডাকে খোকারা সুবিধে করে উঠতে পারতো না। তিনি খুকিদের বলতেন গল্প শুনতে আসতে। আর বলতেন ভাইদের ঘরে রেখে এসো । যে তার যে সুরে বাজে, সে তার সেই সুরেই বাজে । অন্যথা পচে যায় , যেমন আমরা পচে যাই অহরহ ।
সত্যানুসন্ধান কি? ভিলেন কারা কারা ? কাঠগড়ার এপারে ওপারে ।
ফেলুদা, ব্যোমকেশ , কাকাবাবু সন্তু এই সব্বার থেকে আলাদা নোংরা পরী , ডিটেকটিভ রিমা খান । ১) তিনি পুলিশ , সখের গোয়েন্দা নন ২) তিনি মহিলা, প্রথম , একমাত্র মহিলা সত্যানুসন্ধানী বাংলা উপন্যাসের । তিনি ক্ষমতাশালী, ইনফর্ম্যার কনস্টেবল ইত্যাদি প্রয়োগে সমর্থ । যদিও তিনি সাসপেণ্ডেড । ববিটাইজ-করার ভয় দেখাবার প্রক্রিয়ায় নোংরা ।
রাষ্ট্রই ভিলেন নম্বর ওয়ান
এই উপন্যাসে, প্রথম বাংলা উপন্যাসে আমরা দেখতে পেলাম অপরাধ জগতের ব্যক্তিনির্ভরতার ঊর্ধ্বে সিস্টেমটাকে । আমরা দেখতে পেলাম রাষ্ট্র কোথায় অপরাধী । কিভাবে তুরুপ উপজাতির মানুষদের উৎখাত করে ফেলে খনি-মাফিয়া খনির লোভে । কিভাবে ক্যাপিটালিজম এর , ব্যবসায়িক উদারনীতির , শিকার হয় অরণ্যের মানুষ । যাদের রাষ্ট্র কিচ্ছু দেয় না, যাদের "সমাজ" ব্যবস্থা , নীতি ব্যবস্থাকে রাষ্ট্র স্বীকারই করে না , যাদের ভোটাধিকার নেই, পৌরসুবিধা নেই , তাদের কিভাবে অনায়াসে একটি মাত্র পুলিশ চৌকির অন্তর্গত করে ফেলে রাষ্ট্র। মায়া ও নিরঞ্জন যখন তুরুপ গোষ্ঠীর বাচ্চাদের শিক্ষিত করতে থাকেন , কিভাবে সেই মানবিক প্রচেষ্টাকে পুলিশ অবলীলায় বলে "উপজাতিদের পড়াশুনা শিখিয়ে তোমরা যে এই অঞ্চলের ভারসাম্য নষ্ট করছিলে সে সংবাদ আছে আমাদের কাছে ।" এই ভারসাম্য ফেরত আসে , যখন সমস্ত আদিবাসী অরণ্য ছাড়া হয়ে খনি শ্রমিকে পরিণত হয়। কনজিউমার সোসাইটির প্রয়োজন তো সত্যই , কিন্তু আরণ্যক উপজাতির সত্যটুকুর কোনো দাম থাকে না রাষ্ট্রের চোখে । সবুজ নষ্ট হয়ে যায় । মাটিতে বড় বড় হাঁ করা গর্ত তৈরি হয়। কারণ খুঁড়েছে মাফিয়া, কোন বিবেকবান রাষ্ট্র নয় ।
মায়ার "আচ্ছা চলি"র পিছনে রাষ্ট্র নামক ভিলেনের কি অবদান তা বোঝার জন্যে পড়ে দেখুন উপন্যাসটা
ভিলেন নম্বর দুই
বলব না। তাহলে আর কী পড়ে দেখবেন । কিন্তু রিমা বুঝতে পেরেছিলেন ভিলেন কে। কংকাল প্রেমিকের ঘাতক কে । আর সেই ভিলেন কে বানিয়েছিল মধ্যবিত্ত সমাজের হাশহাশ নীতি, শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা । যারা ভালবাসা দেখতে পায় না। ভালবাসার অভাব দেখতে পায় না । পবিত্র বিবাহগ্রন্থির নীচে চেপে রাখতে চায় সব রকম অতৃপ্তির চিৎকার । আর গ্রন্থিমুক্ত হতে চাইলে আঘাত করে সেই মানুষটিকে সুপরিকল্পিত ভাবে।
ভিলেনের স্মৃতিসৌধ
মায়ার "আচ্ছা চলির" পরে , মায়ালিঙ্গার পুলিশের হাতে অত্যাচারিত হবার পরে , তুরুপ প্রজাতির জঙ্গুলে মানুষই পুলিশের হাত থেকে বাঁচিয়ে আনে নিরঞ্জনকে। মায়া ছিলেন তাদের জন্য শিক্ষিকা , মাতৃরূপিণী , জীবন্ত দেবী , আম্মা। আর মায়াগারু সেই দেবীর জীবনের অঙ্গ । তুরুপ গোষ্ঠীর এই মানুষদের সমাজচেতনা আলাদা। তারা মায়া-নিরঞ্জনকে গ্রহণ করেছিল খুব সহজ ভাবে , বর্তমানে নির্ভর করে, তাদের অতীত না খুঁড়ে। তাঁদের চলে যাওয়ার পরে তারা কুঁড়ে ঘরটাকে মন্দিরের সম্মান দেয় । কোন বিগ্রহহীন মন্দির। কিন্তু মায়ার আকস্মিক প্রস্থানের জন্য দায়ী ক্ষমতা গোষ্ঠী , কুঁড়েটাকে ধর্মের দোকান বানিয়ে ফেলে অচিরেই । বহু পরে রিমা খান অকুস্থলে গিয়ে দেখতে পান, এক অদ্ভুত মূর্তি সহকারে মন্দিরটি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে । সেখানে মায়া পাল-এর ভাবমূর্তি বেচে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে খনি-মাফিয়ার দল বেশ দু পয়সা আয়ও করে নিচ্ছে ।
এভাবেই আমাদের দেশে সতী প্রথা থেকে শুরু করে অনার-কিলিং অব্দি বিভিন্ন ভাবে একটি মেয়ের সত্ত্বা ও অস্তিত্ব গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। তারপর তাকে "ধার্মিক" প্রমাণ ক'রে , দেবী প্রমাণ ক'রে, তার ব্যক্তিসত্তা ছিনিয়ে নিয়ে সমাজ তাকে অন্তর্ভুক্ত করে নেয় নিজের মধ্যে ।
যৌনতার অর্ধেক আকাশ ,যান্ত্রিক ও মানবিক অরগ্যাজম , অশ্লীল মলয় রায়চৌধুরী
মায়া
মলয় রায়চৌধুরী সেই অর্থে অশ্লীল যে অর্থে ডি এইচ লরেন্স বা গ্যাব্রিয়েল গারসিয়া মারকেজ অশ্লীল ছিলেন । যখন 'লেডি চ্যাটার্লিস লাভার্স-এ কনির মনে হয় নারীকে তার নারীত্ব থেকে ছিনিয়ে নিচ্ছে আজকের পুরুষ আর সমাজ , বহু বায়বীয় কথার মধ্যে দিয়ে তার শরীরী রহস্য আর দেহোত্তীর্ণতা দুটোকেই নষ্ট করছে, তখন কংকাল প্রেমিক পরম যত্নে ধুইয়ে দেন প্রেমিকার অঙ্গ প্রেমিকার অনুজ্ঞায় , ঋতূস্রাবের পর । এই স্পর্শ আমাদের পরিচিত যৌনতার থেকে অনেক ঊর্ধ্বে । এখানে ভালোবাসা যে-কোনো ইজমকে অতিক্রম করেছে। লজ্জা ঘৃণা ভয় ত্যাগ করেছেন কৃষ্ণ এখানে , শুধু রাধা বা গোপিনীর দল নয় । এই ভালোবাসায় নিরঞ্জন নিষিক্ত হতে থাকেন মায়ার সঙ্গে , সভ্যতা-ছেঁকে পাওয়া সভ্যতায় ।
মিলি
মেয়েদের যৌনতাকে সমাজ সাধারণতঃ অশ্লীল মনে করে। এই উপন্যাস-এ লেখক সেই ঢেকে যাওয়া অর্ধেক আকাশকে টেনে নিয়ে এসেছেন অনেকখানি । নিরঞ্জনের কৈশোরে মিলি , তাদের খেলাধূলোয় কেবল কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা দেখায় না। সে আগে নিজে তৃপ্ত হয়ে নেয় নিরঞ্জনের মাধ্যমে । তারপর নিরঞ্জনকে নিয়ে যায় শিখরে । এই দেয়া নেয়ার সহজ হিসেবটুকু এই টেণ্ডারনেসের সঙ্গে আমি সচরাচর পাই নি কোন বাংলা উপন্যাসে । এই প্রসঙ্গের অবতারণা যখনই হয়েছে, কিছু বিকৃতির সঙ্গে করা হয়েছে । আবার লরেন্সের থেকে ভাবটি উদ্ধৃত করতে ইচ্ছে করে- স্পর্শ ছাড়া কিই বা টিকে থাকে , শেষ পর্যন্ত দেহে মনে অস্তিত্বের শিকড়ে ? যদি স্পর্শ তেমন স্পর্শ হয় ।
রিমা খান
RACHEL P. MAINES এর "The Technology of Orgasm "Hysteria," the Vibrator, and Women's Sexual Satisfaction" রচনা যেটি Johns Hopkins University Press থেকে প্রকাশিত হয়েছিল, তার প্রথম পরিচ্ছেদের নাম হলো " THE JOB NOBODY WANTED " যে-কাজটি-কেউ-চায়নি । শতকের পর শতক মেয়েরা তাদের যৌন চেতনাকে ঢেকে রেখেছে , সেবামূলক ও প্রদান-ভিত্তিক মিলনের আড়ালে। তাই তার চেপে রাখা "হিস্টিরিয়া" টুকুকে কখনোই অনুরণনে পরিণত হতে দেয় নি পিতৃতান্ত্রিক সমাজ । সেটা শুধু চিকিৎসা-সাপেক্ষ গোঙ্গানি হয়ে থেকে গেছে। তাই রিমা খান যখন ডিলডো ব্যবহার করে খুশী হয়, তৃপ্ত হয় , ফুরফুরে হয় , আমি তখন আবার উদ্ধৃত করি " When the vibrator reemerged during the 1960s, it was no longer a medical instrument; it had been democratized to consumers to such an extent that by the seventies it was openly marketed as a sex aid. Its efficacy in producing orgasm in women became an explicit selling point in the consumer market. The women's movement completed what had begun with the introduction of the electromechanical vibrator into the home: it put into the hands of women themselves the job nobody else wanted. " RACHEL P. MAINES এর রচনা থেকে ।
আমি এই "অশ্লীল" , নারীবাদী , মানবতাবাদী লেখককে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি।
উপন্যাসের ফর্ম , Anachronism , সাহিত্যের ডিটেকটিভদের টাইম ট্রাভেল , রাজনৈতিক গণহত্যা ও ডিটেকটিভ বিলাসিতা
টাইম ট্রাভেল ও ডিটেকটিভ দের চোখে সামাজিক অবক্ষয়
এই উপন্যাসে বেশ কটি মজার পয়েণ্ট রয়েছে । Anachronism বা সময়ের হেরফের ব্যবহার করে দিল্লিতে আন্তর্জাতিক ডিটেকটিভ কনফারেন্সে মলয় রায়চৌধুরী আবির্ভূত করেছেন দেশ বিদেশের বহু সত্যান্বেষীকে , সাহিত্যের পাতা থেকে উঠিয়ে তাদের জীবন্ত করে তুলে, তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখাতে চেয়েছেন আজকের সমাজে ডিটেকটিভদের অপ্রাসঙ্গিকতাটুকু ।
দিল্লিতে আন্তর্জাতিক ডিটেকটিভ কনফারেন্সে "প্রায়ভেট ডিটেকটিভ এসেছিলেন চেন কাও , ডেভিড স্মল, নিও উল্ফ, ভি আই ওয়ারশসস্কি, শন স্পেনসার, স্যাম স্পেড, শার্লক হোমস, কিনসে মিলোনে, এরকিউল পয়েরো, লিউ আর্চার, পল আর্টিজান, লিন্ডসে গর্ডন, জো ক্যানোলি, রেক্স কার্ভার, এলভিস কোল, হ্যারি ড্রেসডেন, ড্যান ফরচুন, ডার্ক জেন্টলি, এলেনি কুইন, এমারসন কড, কেট ব্যানিংগান, ক্লিফ হার্ডি, মাইক হ্যামার, টমাস ম্যাগনাম, ভেরেনিকা মার্স, ফিলিপ মারলো, জিম রকফোর্ড, জন শাফ্ট আর ম্যাথিউ শাডার ।" দেবেন্দ্রবিজয় , অরিন্দম , বাংলাদেশের কিশোর পাশা, মাসুদ রাণা আর মুসা আমন; আমাদের হুকাকাশি, কল্কেকাশি, নিশীথ রায়, ইন্দ্রনাথ রুদ্র, জয়ন্ত-মাণিক-সিন্দরবাবু জুটি , গুপি-পানু-ছোটোমামা জুটি, গোন্ডালু, কিকিরা, পাণ্ডব গোয়েন্দা, ট্যাঁপা-মদনা জুটি, গোগোল এরাও সবাই দেখা দিয়েছেন কনফারেন্সে ।
এঁরা সব্বাই একবাক্যে বলেছেন, যেখানে দেশের কোটি কোটি টাকা বিদেশে পচছে , রাজনৈতিক ফুসলানিতে তৈরী দাঙ্গায় মারা যাচ্ছে হাজার হাজার মানুষ , সেখানে খুচরো দু একটা খুনের কিনারা করতে গোয়েন্দা পোষা , বিলাসিতা মাত্র, সরকারের ধুলো দেয়া জনতার চোখে । এইভাবে সাহিত্যের গোয়েন্দাদের মাধ্যমে সাহিত্যের সমালোচনা অভিনব ও বেনজির ।
সংক্ষিপ্ত উপন্যাস এর সুবিশাল গণ্ডী
এই উপন্যাসটি অত্যন্ত চটি , টানটান । এটি সম্ভব হয়েছে একটি বিশেষ ফর্মের কারণে । সেটা হলো , ফ্ল্যাশব্যাক বা ডায়রি-লিখনের মাধ্যমে উপন্যাস এর বেশীরভাগ অংশ বর্ণিত হয়েছে। কঙ্কাল প্রেমিকের অতীত , রিমাখানের বর্তমান, এই দুই এর মধ্যে ঘুরেছে সমস্ত ঘটনা । অতি স্বল্প পরিসরে ভালোবাসা, সামাজিক সমস্যা , রাজনৈতিক কূটকচালি আর একটা লোমহর্ষক গোয়েন্দাকাহিনী এক সাথে বর্ণিত হয়েছে । লেখকের "অরূপ তোমার এঁটোকাটা " উপন্যাসেও ডায়রি লিখনের মাধ্যমে খুব স্বল্প পরিসরে অনেকটা ক্ষেত্র দেখানো গিয়েছিল । এই পদ্ধতিটি বেশ অভিনব বাংলা সাহিত্যে , যদিও কিছু কিছু এমন নজির আছে (যেমন "স্ত্রীর পত্র" শুধু পত্র লিখনের মাধ্যমে জীবনের সত্যিটুকু তুলে ধরতে পেরেছিল )।
পুলিশের গোয়েন্দাগিরির পদ্ধতিটাও খুব ভালো ভাবে ধরা পড়েছে এখানে, যে পদ্ধতি শখের বা প্রাইভেট গোয়েন্দার পদ্ধতির চেয়ে অনেক আলাদা। ইনফরম্যার-এর ব্যবহার, ছিঁচকে অপরাধীকে ভয় দেখিয়ে ছোটখাটো কাজ করিয়ে নেওয়া , ফরেনসিক অ্যানথ্রপলজিস্ট এর মতামত নিয়ে আইনতঃ প্রমাণ সাজানো , দরকার পড়লে অনিচ্ছুক লোকের বাড়ির ফোনের তার কেটে টেলিফোন কোম্পানির লোক সেজে ঢুকে পড়ার ফিকির ইত্যাদি অনেক রকম উপায় সম্পর্কে আমরা অবহিত হই ।
আবার কোন একটি কেস হঠাত করে পুলিশের কাছে দরকারি হয়ে পড়ে কেন, জমির বা রিয়াল এস্টেটের মাফিয়া কেন চায় যে একটা কোন সম্পত্তি দুর্নাম মুক্ত হোক, তা সে সত্যি বার করেই হোক বা বিশ্বাসযোগ্য সত্যি ক'রে , এই নানান জটিলতা ধরা থাকে এই উপন্যাসে ।
মলয় রায়চৌধুরী নিজেই এই উপন্যাসের একটি চরিত্র হয়ে শেষ দৃশ্যে উদয় হন ; কাহিনির সত্যতাকে পাঠকচেতনায় সংশয়ে রাখার প্রয়াসে । আর উপন্যাসের শেষে , অন্ততঃ একজন অপরাধীর উত্তরণ দেখা যায় মানুষ হিসেবে।
শেষকথা
সবটুকু মিলিয়ে বলা যায় যে এরকম প্রেমের উপন্যাস , যা কিনা অনেকগুলি বহুমুখী সত্যের ভিত্তিতে তৈরি করা বহুভূজের মধ্যে আমাদের এক অন্যরকম জীবনচেতনার মুখোমুখি করে দেয়, খুব বেশী লেখা হয় নি বাংলা ভাষায় । বিষয় বৈচিত্র ও সাহসী মনোজ্ঞ বর্ণনায় এই উপন্যাসটি বড্ড আলাদা, উৎকেন্দ্রিক , ঠিক এর লেখকের মতোই । পড়ে দেখতে পারেন সময় করে । মনের জটগুলো খুলে যাবে (অন্ততঃ আমার তো গেছে ) , আলো আসবে মনে।
 রফিক উল ইসলাম | 27.58.255.50 | ১১ আগস্ট ২০২১ ১৯:২৮734862
রফিক উল ইসলাম | 27.58.255.50 | ১১ আগস্ট ২০২১ ১৯:২৮734862রফিক উল ইসলাম
মলয় রায়চৌধুরীর ‘মেধার বাতানুকূল ঘুঙুর’ : এক অন্তর্মুখী পাঠকের ভাবনা
প্রাককথন
নিয়ত এই কবিতাযাপনের ভেতর হঠাৎ কিছু কুশলী কলম
নাড়িয়ে দিয়ে যায় আমাদের । নিত্য থেকে অনিত্যে
পৌঁছোনোর সেই যাত্রাপথ তখন রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে ।
কবিতার ভাব, ভাষা, চিত্রক্লপ অথবা প্রকরণ সবটুকুই
সময় বাহিত । এবং সময়শাসিতও বটে । এর ভেতরেই
কিছু-কিছু ঘুরে দাঁড়ানো, মিছিল থেকে দূরে সরে আপন
সত্ত্বায় ঝলমল করে ওঠে। নতুন-কবিতা-পড়তে-আসা
আমরা, দশ সহস্রাধিক পংক্তি নিয়ে যখন অতলের খেলায়,
হঠাৎ কিছু-কিছু কাব্য আড়ালে ডেকে নিয়ে যায় । সেই
অপরূপ আমাদের মোহিত করে রাখে বহুকাল, এমনকি
হলেও হতে পারে সারাটা জীবন। নিরন্তর কুড়োনো এবং
হাত ফসকে গলে যাওয়ার ফাঁকে-ফাঁকে কোনো-কোনো
মণিরত্নরাজি সারাজীবনের সঙ্গী হবে, এমন প্রশ্নে নির্বাক
হয়ে যাই।
বহুকাল পূর্বে পঠিত 'মেধার বাতানুকূল ঘুঙুর' এমনই
ডেকে নিয়েছিল আড়ালে, নির্বাক করে তুলেছিল ।
কবিতায় তরুণকাল পেরিয়ে আমরা তখন যুবক হব-হব ।
হঠাৎ কেউ হাত রাখলেন পিঠে, আর অমোঘ সেই ডাক,
গম্ভীর অথচ আন্তরিক, তিরের ফলার মতন শাণিত,
ব্যতিক্রমী এবং স্পষ্ট । ফেরার কোনো উপায়ই রইলো
না।
এমনই কবি মলয় রায়চৌধুরী।তখনও পর্যন্ত কিছু-কিছু
কবিতা পড়েছি তাঁর । সেই প্রথম কাব্য পড়ব । আর
পড়তে গিয়েই সমূল কেঁপে ওঠার পালা । পড়তে-পড়তে
চতুর্দিকে ধ্বসে পড়ার পালা। স্মৃতিবাহিত সে-সব
অভিজ্ঞতা স্পষ্ট মনে এল, আজ আবার নতুন করে
কাব্যগ্রন্থটি পড়তে গিয়ে । মনে হল, সেসব কবিতার
নির্মাণ বুকের ভেতর যে সুরম্য বিনির্মাণ গড়ে তুলেছিল,
সবটুকু মুছে যায়নি আজও । যায়নি বলেই বুঝি কবিতা
এমন সদাজাগ্রত প্রহরীর মতন আমাদের তাড়িয়ে নিয়ে
চলেছে; কবিতা থেকে কবিতা এবং কবিতায় ।
কবির আত্মপরিচয়
পৃথিবীর প্রথম পাপের স্পন্দন ঘিরে আমাদের
আত্মপরিচয়। ক্রমে তা ছড়িয়ে পড়ে তৃণ থেকে সাগরে,
সাগর থেকে গ্রহ-গ্রহান্তরে । এই যে ইঁট কাঠ লতা তন্তু আর
দৃশ্য-অদৃশ্য সকল প্রাণী এবং জড়জগৎ সবখানেতেই
আমাদের আত্মপরিচয় পোষিত হয়ে আছে। কোনও এক
মহাপ্রাণ থেকে ছিটকে এসে নিজেকে টুকরো-টুকরো করে
ছড়িয়ে দেওয়া, আর সেই ছড়ানো 'আমি'-কে সাধ্যমতন
কুড়িয়ে আবার মহাপ্রাণে ফিরে যাওয়া--- এইই আমাদের
নিয়তি। একজন কবির নিয়তিও বটে। পূর্ণ থেকে ভগ্নাংশে,
আবার ভগ্নাংশ থেকে পূর্ণে---কোন মহাচালক যে আমাদের
এমন বিচলিত করে, তার হিসেব পাই না। এর ভেতরেই
নিজেদের অস্তিত্ব ঘিরে লড়াই। আর প্রাণে-প্রাণে, পথে-পথে
অস্ফুট গান গেয়ে যাওয়া । যদি কোথাও তা কোনো দিন
লিপিবদ্ধ হয়ে যায় । যদি কোথাও সেই সাধকের আত্মলিপি
গ্রথিত হয়ে যায়।
কবি মলয় রায়চৌধুরী কেমন ভেবেছেন তাঁর আত্মপরিচয়
নিয়ে? খুঁড়ে-খুঁড়ে দেখি। ছিঁড়েকুটে দেখি। অল্প আয়াসেই যা
খুঁজে পাই, তা দেখার পর এতখানি বিস্মিত হব, স্তম্ভিত হব,
স্বপ্নেও তা কি ভেবেছি কোনও দিন?
আলোচনা নিষ্প্রয়োজন । কবিকে উদ্ধৃত করি:
আমি ভূকম্পনযন্ত্র হাণবিক যুদ্ধ দেখব বলে বেঁচে আছি
নীল গর্দভের লিঙ্গ মানবের শুক্রজাত কাফ্রি খচ্চর
(মনুষ্যতন্ত্র পৃ ৩৯)
অথবা
কীটনাশকের ঝাঁঝে মজে-থাকা ফড়িঙের রুগ্ন দুপুরে
ভূজ্ঞানসম্পন্ন কেঁচো উঠে আয়
চাকুর লাবণ্য আমি আরেকবার এ-তল্লাটে দেখাতে এসেছি।
( প্রস্তুতি পৃ ১২ )
অথবা
মরার জন্যে যারা জন্মায় আমি সেই ধর্মবংশ
বাঁচিয়ে রাখার জন্যে বার-বার ঝুলি না ফাঁসিতে ।
( আরেকবার উহুরু পৃ ২৩ )
সময়, হে অশ্বারোহী
একজন কবি কীভাবে লেখেন বিস্তৃত এই কালপ্রবাহ ও তাঁর
সময়কালকে ? দুরন্ত অশ্বারোহীর মতন যে যে সময়
আমাদের চতুশ্পার্শে তুফান তুলে চলেছে, তার কতটুকুই বা
গ্রহণ করা যায় । মর্মে-মর্মে যেধ্বনি জাগরিত, সময়ই তার
আদি এবং প্রকৃত নিয়ন্ত্রক । এই নিয়ন্ত্রণের ভিতরই কবির
চোখ মেলে দেখা । এই ধারাবাহিক গণ্ডি কি পুরোপুরি
ডিঙিয়ে যাওয়া যায় ? অঅতীত আর বর্তমানের, বর্তমান
আর ভবিষ্যতের সূচকরেখায় দাঁড়িয়ে কবি আন্দোলিত
হন, ক্ষতবিক্ষত হতে থাকেন, উজ্জীবিত হয়ে ওঠেন । এই
উজ্জীবনের সামান্য আঁচড় ধরা পড়ে তাঁর কাব্যে, এবং
অবশ্যই তাঁর জীবনধারায় ।তখনই কাব্য ও কবিজীবন
সমার্থক হয়ে ওঠে। প্রকৃত কবির কাছে তাই কাব্য আর
জীবনচারণের আদর্শগত সব পার্থক্য মুছে যায়। কাব্য
থেকেই কবির প্রকৃত মুখ আমরা খুঁজে নিতে পারি। কাব্য
থেকে কবির সমকালকেও খুঁজে নিতে পারি, যা এই বিস্তৃত
কালপ্রবাহে একাকার হয়ে গেছে। এমনকি বিশিষ্ট কোনো
উন্মত্ত সময়, যা ইতিহাস হয়ে আছে, স্মরণীয় হয়ে আছে,
সেসবও কি ধরা পড়ে না কবির কলমে ? সর্বত্রই আড়ি
পেতে দেখি। যেমন পুলিশ আড়ি পেতেছিল সব চিঠিপত্রের
ওপর; আর চতুর্দিকে শুধুই হাতকড়া! আমরা কি ভুলে
গেছি সেই সব দিনগুলোর কথা ? কবিও ভোলেননি। তাঁর
সময়কালের সঙ্গে-সঙ্গে তাই উঠে এসেছে আড়িপাতা আর
হাতকড়ার গল্প; রোমশ সারেঙের গল্পও:
'পুলিশে নজর রাখে এখনও চিঠি খুলে পড়ে
ওপরঅলাহে---হাতকড়া পরে আর কতদিন যাবে
উবু হয়ে আছি চার হাতেপায়ে ঝাঁপিয়ে ধরব টুঁটি দাঁতে'
(ধ্রুপদী জোচ্চোর, পৃ ২২)
অথবা
'ভোর রাতে দরজায় গ্রেপ্তারের টোকা পড়ে
একটা কয়েদি মারা গেছে তার স্হান নিতে হবে'
( অস্তিত্ব পৃ ৪০ )
অথবা
'নৌকোর গোলুই থেকে ছুরি হাতে জ্যোৎস্নায়
বুকের ওপরে বসবে লুঙিপরা রোমশ সারেঙ
নাসারন্ধ্র থেকে বন্দুকের ধোঁয়া
"বল শালা শকুন্তলার আঙটি কোন মাছে আছে ?"...'
(লালসেলাম হায় পৃ ৪৪)
প্রেম লিপ্সা ক্রোধ ইত্যকার প্রবাহ
সবখানেতেই প্রেম আমাদের । সবখানেতেই লিপ্সা ।
ঘাসবীজ থেকে মথের ডানা, চোরাগলি থেকে সুন্দরীর
নাভি। কলম কোথাও সুস্হির থাকে না । ক্রমাগত লিপ্সা
থেকে বিরহ, বিরহ থেকে নতুনতর লিপ্সায় আমাদের
জড়িয়ে পড়তে থাকা। এ যেন চিরকালের খেলা। কবি
সুব্রত রুদ্র লিখেছিলেন: 'সবুজ ঠোঁটের ভেতর থেকে দাঁত
বের করে আমাকে কামড়ে দিল গাছটা।' এমনও হতে পারে
কবির লিপ্সার রঙ ! ভাবলে শিউরে উঠতে হয় । কবি
মলয় রায়চৌধুরীও ব্যতিক্রমী নন। তাঁর সোচ্চার উচ্চারণ
স্পষ্ট, এবং অবগুন্ঠিত নয় । প্রেম ও লিপ্সার ভিতর, মায়া
ও সৌন্দর্যের ভিতর একটি রাগি-চেতনা সর্বদাই তাঁর
কবিতায় মিলেমিশে আছে। সবখানেতেই এক রাগি যুবকের
উপস্হিতি আমরা সহজেই টের পাই। কোনও
আন্দোলনকারী হিসাবে নন, একজন শুদ্ধ কবি হিসাবেই
সেই রাগি যুবকের প্রেম, লিপ্সা অথবা রাগের ধরন খুঁজে
নিতে চাইছি। তাঁকে ঘিরে যে সময়ের আবর্তন, যে অসম্ভব
ধূর্ত আর প্রতারক জীবনযাত্রার আবর্তন, সেই আবর্তনের
ভিতর 'নারী' কেমনভাবে বিস্তৃত হচ্ছে তাঁর কবিতায় ?
যে-কোনো লিপ্সার ভিতরই একটি শুদ্ধ নারীচেতনা
অদৃশ্যভাবে কাজ করে যায় । তাও স্মরণ রাখতে হবে
আমাদের। উন্নত প্রেম কোনো প্রতিবন্ধকতা মানে না । এই
প্রতিবন্ধকতাহীন, আড়ালহীন প্রেম কী ভাবে শিল্পের কাছে
আত্মসমর্পণ করে, তা তো দেখে নিতে হবে আমাদের :
'সঙ্গমের আগে মাদি পিপীলিকা ডানা খুলে রেখে দেবে পাশে'
( প্রস্তুতি পৃ ১২ )
এ পঙক্তি পড়ার পর মনে হল, প্রেম-পরিণয়কে মাটির
সাথে, রূঢ় বাস্তবের সাথে সম্পর্কযুক্ত করে তুলতে চেয়েছেন
কবি । মনের দৃঢ়তা তো আছেই তাঁর । শুধু ইচ্ছে হলেই
হল, সামান্য ইশারার:
'কতদিন ইচ্ছে হব সামান্য ইশারা করে আমার দলের লোকেদের
তোমাকে রাস্তা থেকে জোর করে তুলে নিতে বলি।'
(বাজারিনী পৃ ৩১ )
কিন্তু তাঁর লিপ্সার কাছে এসে থমকে দাঁড়াই। শিউরে উঠি :
'ভিজে শায়া শাড়ি ভেতরের আঁটো জামা
দপ শব্দে জ্বলে ওঠো আগুনের জিভ
চেটে নিক যোনির রেশম দুই মাই
লেলিহান কষ্টে নাভি ঝলসে উঠুক'
( কাঠামোতত্ব পৃ ৩৫ )
এ তো গেল প্রেমের কথা, লিপ্সার কথা । এবার সেই রাগি
যুবকটিকে খুঁজব। যার কোমরে সঙ্গোপনে বাঁধা আছে
পিস্তল; ক্ষুর বা ভোজালি চুপচাপ । আর কাঁধে ঝোলানো
ব্যাগে থরে থরে বোমা সাজানো আছে।এমন যুবককে সঙ্গে
নিয়ে সতত সন্ত্রস্ত থাকতে হয়। যে-কোনো সময়েই লণ্ডভণ্ড
হয়ে যেতে পারে সবকিছু। কেন এত রাগ, অভিমান তাঁর ?
এই সুষমামণ্ডিত পৃথিবীর কোনো অপরূপই কি পারে না
তাঁকে শান্ত রাখতে ? বিস্মিত হতে হয়। যে-জীবন পলাশের
ডালে রঙ ছিটিয়ে দেয়, ঝাউশাখাকে আন্দোলিত করে
তোলে, সে-জীবনের প্রতি কোনও টানই কি নেই তার!
আর এই যে সম্পর্কের বাতাবরণ, যাকে ঘিরে আমরা
প্রস্ফুটিত হতে থাকি, আন্দোলিত হতে থাকি, শিহরিত হতে
থাকি, তা কি কোনোই ছাপ ফেলে না ওই রাগি যুবকটির
মর্মে ! খুবই সঙ্গোপনে ভাবি, 'ধানের বুকের দুধে হাত রেখে'
ভাবি । 'কলাপাতা কি করে খুলে যায় দেখবো সারারাত
ধরে' পড়তে পড়তে ভাবি। কবি মলয় রায়চৌধুরী কী
ভাবছেন আপাদমস্তক ক্রোধ নিয়ে ? ওই রাগি যুবকটি,
যার কোমরে গোঁজা পিস্তল আর কাঁধের ব্যাগে থরে থরে
বোমা, কেন তাঁর কবিতায় সেই ছায়ামুখ ফিরে-ফিরে
আসে! নাকি এই আপাতধ্বংস আর প্রলয়ের আড়ালে
কোনও গূঢ় নবপল্লবের ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি?
'নেকড়ে বালিকার কাছে দীক্ষা নিয়ে দুর্গন্ধ মেখেছি টাকরায়
দুচোখে লঙ্কার গুঁড়ো ছুঁড়ে মারো
মুখাগ্নি করার কালে দেখব না কার থ্যাঁতা মড়া
তপ্ত সাঁড়াশি দিয়ে ছিঁড়ে নাও ধাতুকোষ বংশলোপ হোক'
( নেকড়ে বংশ পৃ ৪৫ )
অথবা
ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠে দাঁড়িয়ে মশাল হাতে এগিয়ে চলেছি আমি
ঘাঁটি-পতনের দিকে
দুপাশে শহর জ্বলছে
কাঁধে শিবলিঙ্গ নিয়ে ল্যাংটো মোহন্ত ছুটছে
( পালটা মানুষ পৃ ২০ )
বাড়িদখলের কথা
'দখল করছি না আপাতত কেননা এখনও অনেক বাড়ি
বাকি'--- এরকম পংক্তি থেকেই একজন কবির সামগ্রিক
শিল্পসত্ত্বা আমাদের কাছে ইঙ্গিতপূর্ণ হয়ে ওঠে। দখল করা
এবং তা অনায়াসে পরিত্যাগ করা অন্য দিগন্তে এগিয়ে
যাওয়ার মধ্যে যে-দৃঢ় আত্মবিশ্বাস আর অপূর্ণতার তৃষ্ণা
খুঁজে পাই, তা একজন প্রকৃত কবিরই ক্ষরণজাত। এর
সঙ্গেই যুক্ত আছে লড়বার মন। আত্মতৃপ্তি যে-কোনো
কবিরই মৃত্যুর কারণ। সুখের কথা, এ-কবি অন্তত সেই
শ্রেণীভূক্ত নন। নিরন্তে অতৃপ্তি তাঁকে পীড়ন করে চলেছে ।
ফলে অনেক দূর এগিয়ে আছেন তিনি। যা-কিছু মুঠোর
ভিতর, অধিকারলব্ধ, সে-সব ছুঁড়ে ফেলে নতুনতর খেলায়
মেতে উঠতে চান তিনি। ফলে তাঁর সৃষ্টি ব্যতিক্রমী হয়ে
উঠতে চায়। সদাজাগ্রত মননের সাথে ক্রোধ মিশিয়ে
যে-বজ্রকন্ঠ অর্জন করেছেন তিনি, একদিন এসবও
পরিত্যাগ করে নতুন বর্ণমালায় ধ্বনিত হয়ে উঠবেন।
সুরম্য এক অলীক প্রাসাদের খোঁজে আমাদের যাবতীয়
গৃহহীনতা । আবার তা হয়তো খুঁজে পেয়েও দু-হাতে ঠেলে
সরিয়ে নবতর প্রাসাদের অন্বেষণ--- এভাবেই চলতে থাকা
সারাটা জীবন। এক জীবনে ঠিক কতগুলো প্রসাদ দখল
করা যায়? কতগুলোই বা পরিত্যাগ করে ডিঙিয়ে যাওয়া
যায় ? উত্তর মেলে না কোথাও। যেমন আমি ভেবেছিলুম,
'ঠিক কতগুলো খড়খড়ি থাকে জীবনে! কতগুলো খোলা
যায়!' কোনও প্রসাদে বন্দি হলেই কবির মৃত্যু--- এমন
ধারণা কি চিরকালের সত্য হয়ে উঠবে ! যদি তাই হয়,
এমন মৃত্যু ইপ্সিত নয় কখনও। তাই এই কবির
'বাড়িদখলের' দিকে সাগ্রহে তাকিয়ে থাকি। একদিন
স্বেচ্ছায় এ-বাড়িও পরিত্যাগ করবেন তিনি, নতুন বাড়ি
দখলের লক্ষ্যে। আমরা তাঁর লক্ষ্যের সাথে নিজেদের লক্ষ্য
জুড়ে গেঁথে দিই:
'দরোজায় লাথি মেরে বেহায়া চিৎকার তুলছি মাঝরাত্তিরে
যারই বাড়ি হোক এটা খুলতে হবেই নাতো ভেঙে ঢুকে যাবো
সামলাও নিজস্ব স্ত্রীলোক-বাঁদি সোনাদানা ইষ্টদেবতা
ফেরেবের কাগজপত্তর নথি আজ থেকে এ-বাসা আমার
ভোর হলে রাস্তায় সমস্ত আসবাব ছুঁড়ে ফেলে দেবো
শষ্যের গ্রীষ্মবর্ষা পাপোষের নারিকেলসারি-ছায়া পোশাকের মেঘলা দুপুর
গয়নার ভালোবাসা বাসনের দিনান্তের ক্ষিদে
সদর দরোজা দিয়ে ধাক্কা মেরে বের করে দোবো
দখল করছি না আপাতত কেননা এখনও অনেক বাড়ি বাকি'
( বাড়িদখল পৃ ১৩ )
( হাওয়া৪৯ পত্রিকার মলয় রায়চৌধুরী সংখ্যা, বৈশাখ ১৪০৮, থেকে পুনঃপ্রকাশিত )
 মলয় রায়চৌধুরী | 122.179.172.247 | ২৪ আগস্ট ২০২১ ১৯:১৫734894
মলয় রায়চৌধুরী | 122.179.172.247 | ২৪ আগস্ট ২০২১ ১৯:১৫734894মহর্ষি এবাদুল হক
মলয় রায়চৌধুরী
এবাদুল হক ছিলেন মহর্ষি, লিটল ম্যাগাজিন সাহিত্যজগতের উদ্ভাবনাকেন্দ্রের মহর্ষি, উন্নতভাবনার, উন্নতমানসের উন্নতধী শিক্ষক । ‘ঋষ্’ ধাতুর অনেকগুলি অর্থের মধ্যে একটি অর্থ হচ্ছে ঊর্ধ্বগতি অর্থাৎ ওপরের দিকে ওঠা৷ কোনও বাড়ির একতলা থেকে ওপরে ওঠার জন্যে এই ‘ঋষ্’ ধাতু ব্যবহৃত হতো৷ ‘ঋষ্’ ধাতুূ‘ইন্’ করে ‘ঋষি’ শব্দ পাচ্ছি, যার ভাবার্থ হচ্ছে যিনি ওপরের দিকে ওঠেন আর যোগার্থ হচ্ছে উন্নতমানস, উন্নতধী,.উন্নত ভাবনার পুরুষ৷ ‘ঋষি’ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ রূপ ‘ঋষ্যা’ হলেও অভিন্নলিঙ্গ (ন্তুপ্সপ্পপ্পপ্সু ন্ধন্দ্বুস্তুন্দ্বব্জ) ‘ঋষি’ শব্দটিও চলতে পারে৷ অর্থাৎ কোন পুরুষকে যেমন ‘ঋষি’ বলা যায় কোন নারীকেও তেমনি ‘ঋষি’ বলা যেতে পারে আবার ‘ঋষ্যা’ তো চলতেই পারে ।উন্নত চেতনার মানুষদের ঋগ্বেদীয় যুগ থেকে ‘ঋষি’ বলে আসা হয়েছে৷ প্রতিটি মন্ত্র যেমন একটি ছন্দে রচিত, অধিকাংশ মন্ত্র যেমন পরমপুরুষের একটি বিশেষ নামে সম্বোধিত, তেমনি প্রতিটি মন্ত্রেরই একজন করে দ্রষ্টা-ঋষি থাকতেন যিনি তাঁর সাধনায় বা ধ্যান-ধারণায় সত্যকে উপলব্ধি করে তা শিষ্যকে কানে কানে শুনিয়ে দিতেন (গোড়ার দিকে অক্ষর ছিল না৷ তাই লিখে শেখানো সম্ভব ছিল না৷ যেহেতু লিপি ছিল না তাই ‘লেখক-ঋষি’ বলা হত না ;বলা হত দ্রষ্টা-ঋষি, অর্থাৎ যে ঋষি ধ্যানে সত্যকে দেখেছেন)৷
ঋগ্বেদীয় যুগ থেকে ঋষিদের মুখ্যতঃ চারটি ভাগে বিভাজিত করে রাখা হয়েছিল–(১) মহর্ষি, (২) দেবর্ষি, (৩) রাজর্ষি ও (৪) ব্রহ্মর্ষি৷ যে সকল মানুষ তাঁদের জাগতিক কর্ত্তব্য যথাবিধি সম্পাদন করার সঙ্গে সঙ্গে ঊধর্বতর জগতের খোঁজে ধ্যান–ধারণা–সাধনা (আরণ্যক ও উপনিষদ) প্রভৃতি করতেন ও তৎসহ সেই অধ্যাত্ম মার্গে সিদ্ধিলাভ করে জগতের সেবা করতেন তাঁদের বলা হত মহর্ষি (যেমন, মহর্ষি বিশ্বামিত্র)৷ (২) যাঁরা দেবকুলে (নর্ডিক, এ্যলপাইন অথবা মেডিটারেনিয়ান উপবর্গীয় ও ককেশীয় বর্গীয় কুলে) জন্মগ্রহণ করে সাধনার দ্বারা আধ্যাত্মিক চেতনায় অধিষ্ঠিত হতেন তাঁদের বলা হত দেবর্ষি (যেমন, দেবর্ষি নারদ) (৩) যাঁরা জাগতিক কর্তব্যের অতিরিক্ত সামাজিক কর্তব্য (যেমন, রাজা) প্রতিপালনের সঙ্গে সঙ্গে নিজের হূদয়বৃত্তিকে...মনীষাকে আধ্যাত্মিক চেতনায় অভিক্লপ্ত করতেন (হূদামনীষা মনসাহভিক্লপ্তঃ) তাঁদের বলা হত রাজর্ষি (যেমন, রাজর্ষি জনক) । এবাদুল হক তাঁর জাগতিক কর্তব্য অর্থাৎ নিজের সংসার প্রতিপালন ও স্কুলের শিক্ষকতার চাপ সত্তেও সাহিত্যের উর্ধ্বতর ধ্যান-ধারণা-সাধনা করে গেছেন আজীবন ।
পৌরাণিক যুগের বহু ঋষিদের নাম আমরা জানি : “পৌর, শ্রুতবিদ, মধুচ্ছদা, জেতৃ, মেধাতিথি, অর্চনানা, অজীগর্ত্ত, হিরণ্যস্তুপ, ঘোর, যজত, প্রস্বম্ব, সব্য, নোধা, শক্তি, পরাশর, সপ্তবধ্রি, রহুগণ, দীর্ঘতমা, দিবোদাস, পুরুচ্ছেদ, উচথ্য, উরুচক্রি, সোমাহুতি, উৎকীল, বাহুবৃক্ত, কুশিক, গাধী, ইষীরখ, বুধ, গবিষ্টি, বসুশ্রুত, ইষ, গয়, সুতম্ভর, সত্যশ্রবা, ধরুণ, মৃক্তবাহ, দ্বিত, বব্রি, প্রযস্বস্বৎ, বিশ্বসামা, দুম্ন, বসুযু, গোপায়ন, পুরুকুৎসা, লোপায়ন, লোপামুদ্রা, সুবন্ধু, শ্রুতবন্ধু, বিপ্রবন্ধু, ত্রিকৃষ্ণ, ত্র্যরুণ, ভরত, গৌরিবীতি, বক্র, অষ্টবক্র, অবস্যু, গাতু, সম্বরণ, স্বস্তি, প্রভুবসু, কশ্যপ, সাদাপৃণ, প্রতিবথ, প্রতিক্ষত্র, প্রতিভানু, শ্যাবাশ্ব, ঘোষা, অপালা, বিশ্ববারা, ভারতী, গার্গী, বীতহব্য, কৃতযশা, দক্ষিণা, ব্রহ্মজায়া, মৈত্রেয়ী, সরমা, সুহোত্র, শুনহোত্র, নর, শুংযু, ঋজিশ্বা, প্রিয়মেধ, সধ্বংসাখ্যা, কপিল, কনাদ, অন্ধ, বৎস, নীপাতিথী, নারদ, সুদিতি, উশনা, ত্রিশোক, দূষ্মীক, ত্রিত, নাভাক, সোভরি, নৃমেধ,অগস্তি, জৈমিন, দার্ঢ়াচ্যুত, ইম্ববাহ, অগ্নিবৈশ্য, বার্হস্পত্য, অত্রি, আত্রেয়, শাতাতপ, অনাবৃকাক্ষ, গার্গ্য, অব্য, সারস্বত, সাংখ্য, আলম্বায়ন, আস্তিক, দেবল, দুর্বাসা, ভূধর, বাল্মীকি, বৈশ্বানর, মার্কন্ডেয়, জমদগ্নি, প্রজাপতি প্রমুখ । আমাদের সময়ে তেমনই হলেন এবাদুল হক । এবাদুল কেবল যে নিজেই উন্নতভাবনার পুরুষ ছিলেন, তাই নয় ; তিনি নিজের সঙ্গে অন্যদেরও উন্নতভাবনায় নিয়ে যাবার প্রয়াস আজীবন চালিয়ে গেছেন । উপরোক্ত ঋষিদের মতনই এবাদুল রেখে গেছেন লিখিত পাঠবস্তু ; কোনও প্রাসাদ, শিলালেখ তৈরি করিয়ে যাননি । তাঁর বাবার নাম জয়নাল আবেদীন আর মায়ের নাম হামিদা ।
এবাদুল হককে মহর্ষি বলেছি বলে অনেকের গায়ে লেগেছে । সম্ভবত তাঁরা নিজেদের এবাদুল হকের চেয়ে উন্নতধী, উন্নতমনা, লোভ-লালসা বর্জিত মনে করেন । তা-ই যদি হবে, তাহলে এবাদুল হককে মহর্ষি বলায় ঈর্ষা কেন? পৌরানিক যুগে অনেকেই ঈশ্বর ও ধর্ম সম্পর্কে জানতে গভীর অরণ্যে তপস্যা করতেন । এনারা তপস্যার বলে সমস্ত লোভ-লালসা ত্যাগ করেছিলেন । এই মহাত্মাদের বলা হতো মুনি । যেইসব মুনি তপস্যাবলে বেদের মন্ত্র প্রকাশ করতে পারতেন, তাদের বলা হতো ঋষি । সুতরাং বোঝা যায় যে, সব ঋষিই মুনি কিন্তু সকল মুনি ঋষি নয় । মুনির স্থান অতিক্রম করেই ঋষির স্থানে অধিষ্ঠিত হতে হয় । এজন্য ঋষিরা ছিলেন মুনিদের থেকে উচ্চস্তরের । ঋষিদের সাতটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে । যথা : ব্রহ্মর্ষি, মহর্ষি, দেবর্ষি, কান্ডর্ষি, রাজর্ষি, পরমর্ষি ও শ্রুতর্ষি ।ব্রহ্ম বা ঈশ্বর সম্পর্কে যেসব ঋষিদের বিশেষ জ্ঞান ছিল, তাদের বলা হতো ব্রহ্মর্ষি । ঋষিদের মধ্যে যারা মহান ও প্রধান ছিলেন তাদের বলা হতো মহর্ষি = মহা + ঋষি । দেবতা হয়েও যারা ঋষি ছিলেন তাদের বলা হতো দেবর্ষী = দেবতা + ঋষি ।বেদের রয়েছে দুইটি কান্ড (জ্ঞানকান্ড ও কর্মকান্ড) এর মধ্যে যে কোন একটির বিষয়ে যাদের বিশেষ জ্ঞান ছিল তাদের বলা হতো কান্ডর্ষি । রাজা হয়েও যিনি ঋষি বা ঋষির মতো আচরন করেন তাকে বলা হতো রাজর্ষি ।পরমব্রহ্ম বা ঈশ্বরকে যিনি দর্শন করেছেন তাকে বলা হতো পরমর্ষি ।যেসব ঋষিগণ শুনে শুনে বেদ মন্ত্র লাভ করেছিলেন তাদের বলা হতো শ্রুতর্ষি । বলাবাহুল্য যে সাহিত্যের জন্য যে ত্যাগ এবাদুল হক করেছিলেন তা আর কেউ করেছেন বলে মনে হয় না ।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাবা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে, খ্রিষ্টধর্মের প্রভাব থেকে ভারতীয় যুবকদের রক্ষার জন্য ১৮৬৭ সালে রাধাকান্ত দেব তাঁকে ‘জাতীয় ধর্মের পরিরক্ষক’ ও ব্রাহ্ম সমাজের ‘মহর্ষি’ উপাধিতে ভূষিত করেন । ১৮৪২ সালে দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী সভা ও ব্রাহ্মসমাজের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। পরের বছর তাঁরই অর্থে এবং অক্ষয়কুমার দত্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। এই পত্রিকায় দেবেন্দ্রনাথকৃত বৃত্তি ও বঙ্গানুবাদসহ উপনিষদ প্রকাশিত হতে থাকে। দেবেন্দ্রনাথের প্রচেষ্টায় প্রকাশ্য সভায় বেদপাঠও শুরু হয়। ১৮৪৪ সালে দেবেন্দ্রনাথ প্রথম ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতি প্রণয়ন করেন এবং পরের বছর থেকে তা ব্রাহ্মসমাজে ব্যবহৃত হতে থাকে। দীর্ঘ শাস্ত্রচর্চার ফলে তিনি উপলব্ধি করেন যে, শুধু উপনিষদের ওপর ব্রাহ্মধর্মের ভিত্তি স্থাপন সম্ভব নয়। তাই ১৮৪৮ সাল থেকে তিনি ক্রমাম্বয়ে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ঋগ্বেদের অনুবাদ প্রকাশ করতে শুরু করেন, যা ব্রাহ্মধর্ম (১৮৬৯) নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ১৮৫০ সালে তাঁর অপর গ্রন্থ আত্মতত্ত্ববিদ্যা প্রকাশিত হয়। ১৮৫৩ সালে তিনি তত্ত্ববোধিনী সভার সম্পাদক নিযুক্ত হন এবং ১৮৫৯ সালে ব্রাহ্মবিদ্যালয় স্থাপন করেন। কিন্তু তিনি নিজের বাবা দ্বারকানাথ ঠাকুরকে শ্রদ্ধা করতেন না, এমনকী দ্বারকানাথ ব্রিটেনে মারা গেলে কোনও খোঁজ নেননি ; দ্বারকানাথকে সেখানেই কবর দেয়া হয় । অথচ দ্বারকানাথ ঠাকুরের রোজগারে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের কাজ করতেন । দেবেন্দ্রনাথের স্ত্রী অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের মা মারা গেলে দেবেন্দ্রনাথ শবানুগমন করেননি । তাঁকে যদি মহর্ষি উপাধিতে ভূযিত করা হয়ে থাকে তাহলে এবাদুল হককে করা হবে না কেন ?
এখানে ‘আবার এসেছি ফিরে’ পত্রিকার নভেম্বর ২০১৯ উৎসব সংখ্যা থেকে এবাদুল হকের লেখা সম্পাদকীয়র অংশ তুলে দিচ্ছি, তা থেকে স্পষ্ট হবে কেন তিনি মহর্ষি : “আবার এসেছি ফিরে আমৃত্যু কথাটি বলে যেতে হবে। ‘আমৃত্যু’ কথাটির ব্যাখ্যা দেওয়া প্রয়োজন । আমি ব্যক্তি এবাদুল ও ‘আবার এসেছি ফিরে’ এক সত্বার দুটি ভিন্ন নাম । কারণ আমার ব্যক্তিজীবন ও পত্রিকার জীবনে অনভ কারোর স্হান কোনোদিন ছিল না । আর এই বয়সে হয়তো কেউ আর আসবেও না । হ্যাঁ, বলে রাখা ভাল আমার সঙ্গে আছেন অগণিত মান্যবর কবিসমাজ । আছেন গবেষক ও কিছু ঋজুদৃঢ় পাঠক । ওনারাই আমার সহায় ও সম্বল । আর আছে শহুরে সভ্যতার দ্বারা লালিত কিছু ঈর্ষাকাতর সাহিত্যের মানুষজন । যাঁরা ভুলে যান ‘আবার এসেছি ফিরে’ পত্রিকার ইতিহাস । ক্ষুদ্র পত্রিকার আঙিনায় এই পত্রিকার যে ইতিহাস আছে তা থেকে বিস্মৃত হয়ে লেখা পাঠান । কিন্তু নিজের পত্রিকা নিয়ে যখন লিটল ম্যাগাজিন সম্পর্কে লিখতে বসেন, তখন এককলম আমার জন্য রাখতে ভুলে যান । কেন এই ঔদাসীন্য? গ্রামে লালিত হয়েও বর্তমানে সদর শহরগুলোতে বাস করেন বলে ? আমি অবশ্য অন্যমানুষ । আমার কোনো দল নেই । কোনো রাজনৈতিক দাদাদের দ্বারা পুষ্ট নই । গোষ্ঠীবাজি করা আমার ইতিহাসে ছিল না । হ্যাঁ, রাজনীতি, সমাজনীতি সম্পর্কে দৃঢ় ধারণা আছে বৈকি । আমি বুঝি পৃথিবীতে শাশ্বত বলে কিচু নেই । আছে মানুষ, আছে মানুষের ভাবনাচিন্তা । সেই ভাবনার দোসর হয়ে তাঁদের স্যালুট জানাতে জানি । আমি কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের দাসত্ব করি না । ধর্মবোধের মধ্যে যেখানে মিলনের সুর আছে, আমি সেখানেই যাই । আমি কোনো ধর্মের তথাকথিত আইডেনটিটি পাওয়ার জন্য লালিত নই ।মুসলমান ঘরে জন্মেছি তাই আমি মুসলমান, আমি একথাই জেনে এসেছি আজীবন ।মান্যতাও দিই । ডোম.চামার ছুঁলে জাত যায় না আমার । এক থালায় খাবার খেতে আমার এতটুকু কুন্ঠা হয় না । হ্যাঁ, আমার কাছে মানুষের ভালোবাসা আর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় প্রাধান্য প্রায়।
তবে, পত্রিকার ব্যাপারে বলি, কারোর খবরদারি একদম পছন্দ করি না । এক্ষেত্রে আমি নিজেকে হিটলারের সাথে তুলনা করি । কারোর উপদেশ আমার কাম্য নয় । কেন এত আত্মকথন ? চল্লিশ বছর সাহিত্যজগতে থেকে দুর্গন্ধ, বস্তাপচা পড়ে পড়ে ক্লান্ত হয়ে গেছি ।জীবনানন্দীয় ধারণা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে ।সুনীল-শক্তির দ্বারা পুষ্টতা আর নয় । ভাঙুন, ভেঙে ফেলুন সাহিত্যের খোলনলচে । নতুন কিছু বলুন, নতুন করে । আর তার জনভই ধরে নিন এলাম ফিরে ।কবি-সাহিত্যিকদের কাছে একান্ত অনুরোধ নতুন ভাবনা চাই ল চাই নতুন আঙ্গিক । গদ্যে-পদ্যে সর্বত্রই আসুক প্লাবন ।”
হাংরি আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল ১৯৬১ সালে আর তার এক বছর আগে জন্ম হয় এবাদুল হকের, ১৯৬০ সালের চৌঠা জানুয়ারি । নিজের শৈশব সম্পর্কে এবাদুল হক যা লিখেছেন, তা বেশ মজার, কেননা এবাদুল ( পূর্ব পাকিস্তান ) বাংলাদেশে গিয়েছিলেন, কিন্তু ভালোলাগেনি বলে মুর্শিদাবাদে ফিরে এসেছিলেন ; এরকম ঘটনা বোধহয় সংখ্যায় কম। স্টোইকসদের থেকে কান্ট পর্যন্ত, একটি সর্বজনীন নৈতিকতার পক্ষে যুক্তি দেয়া হয়েছিল । তাছাড়া ঐতিহাসিকভাবে গঠিত সমাজে নানা রকমের মানবতার বিভাজন সত্ত্বেও, মানুষের সাথে নিজেকে চিহ্নিত করা এবং মানবতার জন্য নৈতিক উদ্বেগ থাকা স্বাভাবিক । বিশ্বজনীনতার প্রধান কাজ হল এই যে তা সার্বজনীনতাকে রক্ষা করে । এবাদুল হক শৈশবে এই বোধের কারণে ফিরে এসেছিলেন পূর্ব পাকিস্তান থেকে। এবাদুল হক বুঝেছিলেন, ‘প্রলয়’ পত্রিকা প্রকাশের সময় থেকে, যে, অনুভূতির মূর্ত অবস্থাগুলো - ভালবাসা, ব্যথা, আনন্দ, কৌতূহল, যন্ত্রণা, অহংকার - সবই সাহিত্যে পাওয়া যায় । সাহিত্যে তা এত ভালভাবে বর্ণনা করা হয়, এত তীব্রভাবে যে উনি অনুভব করেছিলেন, এবং বেশ গভীরভাবে, এমন-কিছু যা হয়তো অনেক বছর আগে কেউ অনুভব করেছিলেন। এই বোধ এবাদুলকে জানিয়েছিল যে মানুষের অভিজ্ঞতা ভাগ করা জরুরি । কেননা তা সান্ত্বনা দেয়, পাঠককে স্পর্শ করে এবং বর্তমান দুঃসময়ে তাকে অনুপ্রাণিত করে। অতীতে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলী পাঠকের বর্তমানকে রূপ দিতে পারে।
ওনার ভাষ্যেই শোনা যাক : “তখন আমি ক্লাস সিক্স। আমরা যেমনটি আট ভাই এক বোন। আমার কাকা জ্যেঠারা তেমনটিই আট ভাই দুই বোন । পাঁচ জ্যেঠা এক কাকা আর একজন পিসিমা বাংলাদেশে বিনিময় করে চলে গেছিলেন। আমার আব্বা এখানকার ২১ বিঘা জমি বিনিময় করে দুই দাদাকে সঙ্গে দিয়েছিলেন। আব্বা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। তাছাড়াও এখানকার কংগ্রেসি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আমার তিন দাদা দুই ভাই এখানে থেকে গেলাম। বাংলাদেশের রাজশাহীতে আমার দুই বড় দাদা চাকরি পেয়ে গেছিল। কিন্তু বাড়িঘর করতে পারেননি। ল কাকার বাড়িতে এক দাদা আর একজন আমাদের গ্রামের মানুষ, এখান থেকে যাওয়া ওদের বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করেছেন। আমি ছাত্র হিসাবে খারাপ ছিলাম না। বাড়ির সবাই বলতেন, আট ভাই এক বোনের মধ্যে আমার ব্রেন শার্প । কঠিন পড়া সহজে ক্যাচ করতে পারতাম। মেধা ছিল। তাই বাংলাদেশে নিয়ে গিয়ে রাজশাহীর কোর্ট একাডেমিতে ভর্তির আবেদন জমা দিলাম। ভর্তির পরীক্ষা দিয়ে তের জনের মধ্যে আমি দ্বিতীয় হয়েছিলাম। ১৯৭০ সাল। ভাষা আন্দোলন আর তথাকথিত ভাষা আন্দোলনে সীমাবদ্ধ থাকেনি। স্বাধীন সার্বভৌমত্বের দাবী করে শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে জোর আন্দোলন। মিটিং মিছিল থেকে শুরু করে আইন অমান্য সবকিছু হচ্ছিল। একমাস ক্লাস করার পরেই স্কুলে অশান্তি। উঁচু ক্লাসের ছাত্ররা মুক্তিযুদ্ধের ডাকে সাড়া দিয়ে ক্লাস বয়কট করল। চলল পুরো দশদিন। চুপচাপ ঘরে কাঁহাতক বসে থাকা যায়। খুব বোরফিল করছিলাম। হঠাৎ শোনা গেল বিদ্যালয় খুলছে। কিছুদিন ক্লাস করে বুঝতে পারলাম, না এখানকার জল -হাওয়া, বিদ্যালয়ের পরিবেশ আমার স্যুট করবে না। আমি দূরন্ত ছিলাম ভেতরে ভেতরে কিন্তু বাইরে খুব লাজুক ছিলাম। ঠিক লজ্জাবতীর মত। যেমন হাত দিলেই নিজেকে গুটিয়ে নেয়। আমিও বাইরের দিকে গুটিয়ে রাখা স্বভাবের ছিলাম। এখন পর্যন্ত ওই রকমের থেকে গেছি। যারা এগিয়ে আসে তাদের সঙ্গে পিরীত হয়। গায়েগোছে বন্ধুত্ব নৈব নৈব চ। তাই আমার বন্ধুর সংখ্যা হাতেগোনা। পঁয়তাল্লিশ বছরের পত্রিকা সম্পাদনার পরেও সব লেখকদের কাছে পৌঁছাতে পারিনি। সে যাইহোক, পারলাম না, রাজশাহী থেকে পালিয়ে আসতে বাধ্য হলাম। সদ্য ইণ্ডিয়া থেকে পাকিস্তানে যাওয়া আত্মীয় স্বজনেরা কেমন ধারার হয়ে গেছে। এমনকি মুখের কথাতেও যেন কেমন তথাকথিত ভদ্রতার প্রলেপ পড়েছে। এখনও রাজশাহীর ভাষা আমাদের মুর্শিদাবাদের ভগবানগোলার ভাষার মত। এখনও রাজশাহীতে আমাদের মতই কথ্য ভাষার প্রচলন রয়েছে। কোভিড ১৯ এর দুতিন মাস আগে বড়দা এসেছিলেন। ব্যাঙ্কে চাকরি থেকে অবসর নিয়ে মক্কা পরিদর্শন করে ইণ্ডিয়া এসে সকলের সঙ্গে দেখা করে গেছেন। কই তাঁর বলনে - চলনে কোন পরিবর্তন তো আসেনি। আমার থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল আমার কাকার বাড়িতে। কি ক্রমবর্ধমান কৃত্রিম হয়ে ওঠেছে গোটা পরিবার। ক 'বছরের মধ্যে কি সাবলীল অদ্ভূটে পরিবর্তন। এখানে থাকতে মাটির গর্তের পায়খানা ব্যবহার করত। ছেলেরা অধিকাংশ বর্তন হাতে উঁচু নবাবী বাঁধের জঙ্গলের ভিতর ঢুকে পড়ত। ভূতরাজের আকাট জঙ্গল। এখনও সবুজ নধর পাতার গন্ধ নাকে আসে। মন উদাস হয়ে যায়। বনকুলের জঙ্গলে পাকা কুলের ঝোঁপে বনবাটুল, ঘুঘুর আনাগোনা। লক্ষ্মীপুরের বাসায় মোজাইক বসানো সেনেটারি পায়খানা। ঝাঁচকচকে। বয়সে আমার বড় কাকাতুতো বোন শিরীন বলেছিল, এই ছোঁড়া পায়খানায় গেলে বেশি করে পানি ঢালবি। খুব সহজ কথা কিন্তু আমার আঁতে লেগেছিল। একি কথা? আমি ভালো করে টয়লেট পরিস্কার না করেই একগুচ্ছের নোংরা রেখে চলে আসব ? দ্বিতীয়ত দাদারা অফিস চলে গেলে ডাইনিং টেবিলে নাস্তা খাবার ডাক পড়ত। ল কাকীমা মেয়েদের কারো নাম করে ডেকে বলতেন - " অলকা, শিরীন, ডলি কইরে, কোথায় আছিস, এবাদুলকে পাঠাইয়া দে নাস্তা করে নিক। "-প্রসঙ্গত বলি, এখানে থাকাকালীন ওরা কুনঠে > কোথায় , প্যাঠিয়ে > পাঠাইয়া, লাহারি> নাস্তা, লেক > নিক অর্থাৎ শুদ্ধ উচ্চারণে অভ্যস্থ হয়ে উঠেছে। আমার কথা শুনে চোখ টিপাটিপি করে একে অপরের দিকে তাকিয়ে হাসাহাসি করত ; তা এখনও চোখের সামনে উজ্জ্বল হয়ে ভাসে। এমন উচ্চারণ শুনেছি, অতিমাত্রার হয়ে বিসদৃশ্য মনে হত। আমি মনকে শান্ত করতে পারিনি। কাকীমা মুখের সামনে বিপরীত টেবিলে বসে। আমি সামনে গিয়ে বসলাম। টেবিলটা আমার উচ্চতার তুলনায় একটু বেশি। তবুও বসলাম। একটা চিনা খালি থালা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন - " তোমার তো পান্তা ভাত ( আমরা এখনও বাসি ভাত বলি ) খাওয়া অভ্যেস,পরোটা ফরোটা খাও না, দেখ কেমন লাগে। " ছোট্ট পাতলা সাইজের একটা পরোটা আর থালার একপাশে ঝাল আলুর দম তুলে দিলেন। চিবোনা কঠিন হয়ে পড়ছে। কারণ পান্তা ভাতের খোঁচা খিচখিচ করে বুকে বিঁধছে। ল কাকীমা গামলার ঢাকনা তুলতে তুলতে বললেন - " আর নিবা? " মেজাজ টংয়ে। বলেন কি। আমি এধরনের পরোটা চারটি খাব, আর একটা দিয়ে বলেন কিনা, আর একটা দিই ? আমি হাত নেড়ে বলছিলাম, না না আর খেতে পারব না।”
যাঁরা অন্য রকম লিখছেন বা লিখতে চাইছেন, তাঁদের সম্পর্কে এবাদুলের আগ্রহ ছিল সেই ক্লাস নাইনে পড়ার সময় থেকে যখন উনি ‘প্রলয়’ নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ আরম্ভ করেন । ‘প্রলয়’ নামটি থেকেই এবাদুল হক স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে তিনি ভবিষ্যতে সাহিত্যজগতে কী করতে চলেছেন । ‘প্রলয়’ পত্রিকার জন্য তিনি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা সংগ্রহ করে এনে প্রকাশ করেছিলেন ।এরপর ১৯৭৭ সালে যখন উনি ‘রামধনু’ নামে একটা পত্রিকা বের করা আরম্ভ করেন, তখন ওনার কেবল সতেরো বছর বয়স । পত্রিকাটা কোনো কারণে বন্ধ হয়ে যায় এবং ১৯৭৯ সালে আবার প্রত্রিকা সম্পাদনা আরম্ভ করেন । আগের পত্রিকা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বলে নতুন ত্রৈমাসিকটির নাম রাখলেন ‘আবার এসেছি ফিরে’ । একদিকে বট গাছ অন্য দিকে পাকুড় গাছ মাঝ দিয়ে রাস্তা, একটু এগিয়ে বাঁ দিকে পুকুরপাড়ে ছিল ‘আবার এসেছি ফিরে’ আর ‘এবং পুনশ্চ’ পত্রিকা দুটির আশ্রম ।
মুর্শিদাবাদের সীমান্তবর্তী ভগবানগোলার কানাপুকুরে ছিল এবাদুলের বাড়ি আর সেখান থেকেই পত্রিকা প্রকাশ করতেন । কলকাতা থেকে বহুদূরে একটি প্রায়-গ্রামে বসে যে সাড়া ফেলে দেয়া যায় তা ‘আবার এসেছি ফিরে’ পত্রিকার মাধ্যমে দেখিয়ে দিয়েছিলেন এবাদুল । স্হানীয় স্কুলে শিক্ষকতা করতেন এবং অবসর নিয়ে আরেকটি পত্রিকা, কেবল কবিতার জন্য, নতুন কবিদের সবাইকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে দেবার সুবিধার জন্য ‘এবং পুনশ্চ’ নামে, প্রকাশ করা আরম্ভ করেন । আমার ‘আভাঁ-গার্দ’ কবিতাগুলো প্রকাশ করার সাহস ছিল এবাদুল হকের । কলকাতায় তো বহু হামবড়ুয়ে সম্পাদক জানেনই না কাকে আভাঁ গার্দ বলে । তিনি ঋষি এইজন্যই যে স্কুলের ছাত্ররা তাঁর কাছ থেকে নিজেদের সন্দেহ দূর করতে পারতো । তিনি মহর্ষি এই জন্যে যে দুটি পত্রিকার সম্পাদক হওয়া সত্তেও দাদাগিরি ফলাতেন না, কাঁচি চালাতেন না, দল গড়ে নেতাগিরি ফলাতেন না, যা অধিকাংশ লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদকের চরিত্রে দেখা যায় । সংসারের খরচপত্র যতটুকু হয়, তা করার পর নিজের সমস্ত আয় খরচ করতেন ‘আবার এসেছি ফিরে’ আর ‘এবং পুনশ্চ’ পত্রিকা দুটির জন্য । মনে রাখতে হবে যে পত্রিকা দুটির কলেবর ক্ষীণ হতো না ।
বিয়াল্লিশ বছর পত্রিকা সম্পাদনা করে ১৭ই মে ২০২১ তারিখে এবাদুল হক মারা গেলেন করোনা রোগে । দুর্ঘটনার দরুন প্রচুর ওষুধ খেতে হতো এবাদুলকে । মুর্শিদাবাদের বাইরে সাহিত্য সভাগুলোয় যাবার সময়ে ওষুধের ডিবে নিয়ে বেরোতেন । শরীরের সমস্যা দেখা দিয়েছিল ১২ই মে এবং তাঁকে মুর্শিদাবাদ নার্সিং হোমে ভর্তি করা হয় যেখানে তাঁর করোনা পজিটিভ ধরা পড়ে । করোনায় যা হয়, দেহে প্রবেশ করার দিন পনেরো পর আচমকা কাবু করা আরম্ভ করে । এবাদুলের হার্টে ব্লক ছিল, যা উনি মোটর সাইকেল দুর্ঘটনা পর বইছিলেন, কেননা উনি মারা যান হৃদরোগে । এবাদুল হক ছিলেন তরুণতমদের ছত্রছায়া । বিশ্বাস করতেন তারুণ্য-শক্তিই পারে নতুন-যুগের আগমন ঘোষণা করতে । এবাদুলের মতন নির্মোহ নির্লোভ মানুষ পাওয়া বিরল। তিনি ছিলেন বিরলপ্রজ মানুষ । তাই আমি তাঁকে বলেছি মহর্ষি ।
মোটর সাইকেল দুর্ঘটনা এবং আরেকটি দুর্ঘটনা সম্পর্কে এবাদুলের বয়ানই শোনা যাক : “ভয় ব্যাপারটা আমার খুব কম। তবুও সাইকেল, মোটর বাইক, আমার কাছে অচ্ছুত ছিল। অথচ কে জানে, আমারই মোটর বাইক দূর্ঘটনা হল। পেছনে বসে ছিলাম। পাড়ার ভাগনে গাড়ি চালাচ্ছিল। ৯ জানুয়ারি ২০০৭ সাল। কুয়াশাভরা শীতের সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত নেমে আসছে। বহরমপুর প্রেসে সারাদিন পত্রিকার ফাইনাল কাজ সেরে বাড়ি ফিরছিলাম। সামনের দিক থেকে একটা লরি আসছিল। আমার ভাগ্নে যথারীতি নিজস্ব সাইড দিয়েছে, অন্যদিকে পেছন দিক থেকে একটা লরি এসে আমাদের মোটরসাইকেলে ধাক্কা মেরে দিল। আমার উপরে আমাদের বাইক পড়ে গেল। আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। ভাগ্নে সামনের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে জঙ্গলের মধ্যে পড়েছিল। তারপর যা ঘটেছে সবই আমার অজানা। পরে যতটুকু জেনেছি তা প্রত্যক্ষ দর্শকের কাছ থেকে। পেছন দিক থেকে আসছিলেন অশোক রায় নামে এক ভদ্রলোক। বানজেটিয়ায় বাড়ি। আমাদের ঘিরে আছেন চায়ের দোকানে আড্ডাবাজ কিছু ব্যক্তি। অশোক বাবু এসে স্কুটি থামিয়ে সবাইকে ধমকে আমার উপর থেকে মোটরবাইক তুলেছিলেন। সবাই ভেবেছিলেন মারা গেছি। পুলিশ না এলে হাসপাতালে নেওয়া যাবে না। কিন্তু অশোকবাবু জোর করে আমাকে হাসপাতালে নিয়ে গেছিলেন। আমার কাঁধে সবসময়ই শান্তিনিকেতনী ব্যাগ থাকে। সেই ক্লাশ নাইন থেকেই। তো ব্যাগটাই আমার আশ্রয়স্থল। সবকিছু ব্যাগেই থাকত। একটা ক্যামেরা সবসময়ই । সেদিন ব্যাগের মধ্যে ছিল ত্রিশহাজার টাকা এবং খরচের জন্য আলাদা কিছু খুচরো টাকা পয়সা। ব্যাগটা কাঁধেই ছিল। অশোকবাবু নিজ হেফাজতে নিয়েছিলেন। মোবাইলও ছিল। মোবাইল নিয়ে কল লিস্ট ঘেটে দেখছিলেন বহরমপুরের কেউ চেনাশোনা আছে কিনা। ভাগ্নের কাছে জেনেছিলেন আমার সংক্ষিপ্ত পরিচয়। সেই ভরসায় তিনি কললিস্ট সার্চ করে একদা আনন্দবাজারে সাংবাদিক অনল আবেদিনকে ফোন করেছিলেন। অনলদা আবার আমার প্রেসের মালিক গল্পকার অংশুমান রায়কে ফোন করে। তারপর অংশুমান আমার বন্ধু পত্রিকার সহসম্পাদক এমদাদউল হক ( ইন্দ্রপ্রস্থে থাকত ) কে ফোন করে। ছুটে আসে সকলে। আমি অজ্ঞান অবস্থায় ছিলাম। ডাক্তার দেখেছেন। নীলরতন হাসপাতালে রেফার করে দিয়েছেন। আমার হিপ জয়েন্ট চুরমার হয়ে গেছে। ডান হাতের কাঁধ ভেঙ্গে গেছে। ডান পা ভেঙ্গে খানখান। রক্তাক্ত শরীর। ক্ষতবিক্ষত। আমি জানিনা কিছুই। আমার যখন জ্ঞান ফিরল তখন আমি নীলরতন হাসপাতালে ইমারজেন্সী ওয়ার্ডের ওয়েটিং রুমে। আমার সঙ্গে আমার বন্ধু এমদাদউল হক। সে জ্ঞান ফিরে পেতেই কি যন্ত্রণা শরীরে। ঈশ্বর যদি থাকেন তিনিও হয়তো এই যন্ত্রণার পরিমাণ পরিমাপ করতে পারেননি। না হলে অন্ততপক্ষে একফোঁটা জলও গড়িয়ে পড়ত।আমি শীতল হতাম। আমি চিৎকার করে উঠলাম। চেঁচিয়ে উঠে আল্লা, মাগো মরে গেলাম। জীবনে দ্বিতীয়বার আল্লাহ্ শব্দটা উচ্চারণ করেছি বোধহয়। আরেকবার আমার কলিগ শিক্ষকবন্ধু ভাগ্যধর দাস কর্মকারের বিয়েতে বরযাত্রী গেছিলাম বর্ধমান। যে গাড়িতে গেছিলাম সেটি নড়বড়ে। যাইহোক বিয়ে বাড়ির অব্যবস্থায় সারারাত মন বিষাক্ত করে তুলেছিল। বাড়ি ফেরার পথে ড্রাইভার, মেজাজ হারিয়ে সোজা গর্তে নামিয়ে দিয়েছিল। সারারাত আমাদের সঙ্গে ড্রাইভারও উপোস দিয়েছে। বিয়ে শেষ হয়েছে গভীর রাতে। আমাদের যখন খাওয়ার ব্যবস্থা করেছিল তখন প্রায় শেষ রাত। আমরা কেউই খেতে পারিনি। বিয়ে বাড়ির লোকজন ড্রাইভারের খোঁজখবর নেয়নি। ফলে সকালবেলায় বরবন্ধুর কাছে বিদায় নিয়ে গাড়িতে। বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে ফুটিসাঁকো স্টপেজে গাড়ি দাঁড়িয়ে পাউরুটি আর গরম গরম দুধ চা। মিষ্টির দোকান থেকে কিছু মিষ্টি আর পরোটা বেঁধে নিলাম। একটা ফাঁকা জায়গাই গাড়ি দাঁড়িয়ে পরোটা মিষ্টি খেলাম। ড্রাইভার কোনমতেই নিলেন না। অনেকখানি রাস্তা পেরিয়ে তারপর তো বাড়ি। মেজাজ টকেছিল তার। মেজাজে গাড়ি জোরে চালাতে গিয়ে খাদের গভীরে। সামনের একটা চাকা খুলে বনবন সামনের দিকে। হেলে পড়েছে গাড়ি। আমি ড্রাইভারের পাশের সিটে ছিলাম। সবকিছু দেখতে পাচ্ছি। চোখের সামনে দিয়ে নেমে পড়ছে গাড়ি। মাথা ভেতর ঘুরপাক খাচ্ছে। হঠাৎ গাড়িটা উল্টাপাল্টা খেয়ে জোরে ধাক্কা মেরে দাঁড়িয়ে পড়ল। লাফিয়ে উঠল গাড়ি। আমার মাথাটা গাড়ির ছাদে গিয়ে ধাক্কা মারতেই ইয়া আল্লাহ্ বলে নাকি চিৎকার করে উঠেছিলাম। অজ্ঞাতে অজান্তেই। আর এখানে এই হাসপাতালে। আল্লাগো মাগো। কথায় আছে না, ঠেলার নাম বাবাজী।” ২০১৬ সালের পথদুর্ঘটনায় মারাত্মক জখম হওয়ার পর বন্ধ হয়ে গেছিল, ‘আবার এসেছি ফিরে’ আর ‘এবং পুনশ্চ’। দুটিকে ফিরিয়ে এনেছিলেন এবাদুল হক। নিজের খরচে পত্রিকা দুটি প্রকাশ ও সম্পাদনা করতেন, কোনও বিজ্ঞাপন থাকতো না পত্রিকাতে। শুধু লেখা প্রকাশ করা নয়, লেখক কপিও নিজের খরচে লেখককে পোস্ট বা বিভিন্ন উপায়ে পৌঁছে দিতেন। নিজের প্রচুর গল্প নাটক লেখা থাকলেও তিনি তা নিজ পত্রিকায় প্রকাশ করতে সঙ্কোচ বোধ করতেন। নতুন লেখকদের আত্মপ্রকাশের জায়গা করে দেওয়াই তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল।
সাহিত্য নিয়ে যেভাবে কাজ করছিলেন, খুব কম সময়ের মধ্যেই পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন। সাহিত্যের জন্য কখনো এবাদুল হকশহরমুখী হতে চাননি। বাণিজ্যিক কাগজে লেখা প্রকাশেও তাঁর আগ্রহ ছিল না। কাউকে ধরাধরি করেননি কখনও । পৌরাণিক ঋষিদের মতন নিজেকে নিজেই সুশিক্ষিত করেছেন নিজের স্বভাবসিদ্ধ গরিমায় । কলকাতা থেকে বহুদূরে এক মফসসল এলাকায় বসবাস করেও যে পত্রিকা তিনি প্রকাশ করতেন তা ছিল ঋষিতুল্য কর্মোদ্যম ও আত্মাভিমানের প্রমাণ । ‘আবার এসেছি ফিরে’ পত্রিকার এক একটি সংখ্যা প্রায় হাজার পৃষ্ঠার বা তারও বেশি হতো। একজন কবি, প্রাবন্ধিক বা গল্পকার তিনি যত নতুন লেখকই হোন না কেন, তাঁর পত্রিকায় সমান মর্যাদা পেতেন। কলকাতা ও জেলাশহরের দলবাজ নেতা-সম্পাদকদের দ্বারা উপেক্ষিত, অপমানিত, অপরিচিত-নামের প্রান্তিক লেখকদের তিনি বিশেষ সম্মান ও মর্যাদা দিতেন । তিনি তাঁদের নিয়ে পত্রিকার বিশেষ সংখ্যাও করেছিলেন। আগামীতেও কয়েকটি সংখ্যা করবেন বলে লেখা সংগ্রহ করছিলেন। অজিত রায়, রবীন্দ্র গু্হ প্রমুখ, যাঁরা ভিন্নধর্মী গদ্যবিন্যাসের কারণে কলকাতার পত্রিকাগুলোর ডাক পান না, তাঁদের কাছ থেকে গদ্য চেয়ে এবাদুল হক প্রকাশ করেছেন নিজের পত্রিকায় । বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেছেন দেবী রায়, অজিত বাইরী, কবিরুল ইসলাম, বেণু দত্ত রায় প্রমুখকে নিয়ে । রাণা চট্টোপাধ্যায়, অনন্ত রায়, পুষ্পিত মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে সংখ্যা করার জন্য প্রবন্ধ সংগ্রহ করা আরম্ভ করেছিলেন ।
‘আবার এসেছি ফিরে’ সাহিত্য পত্রিকার জন্য ১৯৯২-৯৩ সালে পর-পর দুবার এবাদুল হক পেয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এর ‘সারা বাংলা শ্রেষ্ঠ লিটিল ম্যাগাজিন সম্মান’, ১৯৯৪ সালে পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র যুব উৎসব পুরস্কার, ১৯৯৫ সালে নিজের লেখা নাটকের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একাঙ্ক নাটক পুরস্কার, ২০১৩ সালে অদ্বৈত মল্লবর্মণ জ্মশতবর্ষ স্মারক পুরস্কার, ২০১৬ সালে সারা ভারত লিটল ম্যাগাজিন প্রতিযোগীতায় সাদাত হাসান মান্টো পুরস্কার এবং ২০২১ সালে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমির দেওয়া শ্রেষ্ঠ লিটল ম্যাগাজিনের পুরস্কার । এই পুরস্কারটি সাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবী তুলে দিয়েছিলেন এবাদুল হকের হাতে । এছাড়াও বিভিন্ন জেলার লিটল ম্যাগাজিন পুরস্কার পেয়েছিলেন এবাদুল ওঁর পত্রিকার ডাকাবুকো সম্পাদনার জন্য।
ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা জনিত কারণে কয়েক বছর যাবৎ তিনি অত্যন্ত অসুস্থ ছিলেন। কিন্তু তাঁর ছিল অদম্য মনোবল । শরীরের সমস্যা কোনোদিন তাঁর সাহিত্যকর্মকে প্রভাবিত করতে পারেনি। তাঁর কাজের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ১৭টি নাটকের সংকলন ‘এখনও লক্ষিন্দর’ এবং প্রায় একশটি গল্পের সংকলন ‘অনন্ত’ । নিজের লেখা নাটকে অভিনয় করেছেন।। তাঁর কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা সাতটি । সেগুলি হল ‘কবিতা ও কাকলি’, ‘সূর্যাস্তের আগে ও পরে’, ‘নাগকেশরের ফুল’,’অগ্নিজল’, ‘বাউলজল’, ‘এক গ্লাস জলের ছায়া’ আর ‘পলাতক ছায়া। 'একগ্লাস জ্বলের ছায়ায়' গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতাই ভার্স লিবরে আঙ্গিকে লেখা । তিনি উপন্যাসও লিখতে শুরু করেছিলেন । মুর্শিদাবাদের ডোমকল শহরে ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১ অনুষ্ঠিত হয়েছিল একটি সাহিত্য সভা। এবাদুল হক তাঁর স্বাগত ভাষণে তরুণ ফেসবুকীয়া কবিদের বলেন যে কবিরা তাঁদের নিজস্ব ভাবনা ও ভঙ্গিতে কবিতা লিখবেন , তা কেউ ভালো বলুক বা না বলুক, কিন্তু কারো নকল বা কপি করে নিজের নামে চালিয়ে দেওয়া কখনই উচিত নয় । ২০১২ সালে যখন সারাবাংলা লিটিল ম্যাগাজিন প্রতিযোগিতায় ‘আবার এসেছি ফিরে’ প্রথম স্থান অধিকার করেছিল সেইদিন রবীন্দ্রসদন চত্বরে স্টেজে ছিলেন জয় গোস্বামী এবং মহাশ্বেতা দেবী । পুরস্কার দেবার সময়ে ‘আবার এসেছি ফিরে’ পত্রিকাকে মফসসলের পত্রিকা বলে উল্লেখ করা হলে, এবাদুল হক চিৎকার করে বলেছিলেন “মফসসল কথাটা আপনারা ব্যবহার করবেন না ; আমি মফস্বল থেকে এসছি এবং ‘আবার এসেছি ফিরে’ আপনাদের কাছে আজ মফস্বল থাকলো না।” এবাদুল হক এমনই ডাকাবুকো মানুষ ছিলেন। যা বলতেন সামনাসামনি এবং সত্যি কথাটা জোর দিয়ে বুঝিয়ে দিতেন, বলে দিতেন, কারও তোয়াক্কা করতেন না। কিন্তু সব কিছুর চেয়ে বেশি, এবাদুলের কাছে সাহিত্য ছিল মানবসংযোগ। পত্রিকার সূত্রে অখ্যাত অথচ অসাধারণ ব্যক্তির সংগে যোগাযোগ ঘটেছে তাঁর, অখ্যাত হলেও যাদের কাছ থেকে নতুন কিছু শেখা যায় ; যাদের সাথে মিশে হাসা যায় এবং আনন্দ ভাগাভাগি করা যায় ।
মহর্ষি এবাদুল হকের সঙ্গে আমার পরিচয় বহুকাল আগে । গ্রামীণ উন্নয়নের চাকুরির সূত্রে আমি যখন বদলি হয়ে কলকাতায় ফিরি, তখন নাকতলার ফ্ল্যাটে থাকতুম । আমি কলকাতার সাহিত্যজগতকে এড়িয়ে চলতুম বলে কবি-লেখকদের বিশেষ আনাগোনা ছিল না আমার ফ্ল্যাটে । একদিন হঠাৎই এক যুবক এলেন, নিজের নাম বললেন এবাদুল হক, এসেছেন মুর্শিদাবাদের কানাপুকুর থেকে, আমার লেখা চান আর আমাকে নিয়ে ক্রোড়পত্র প্রকাশ করতে চান । যুবকটির প্রস্তাব ছিল স্তম্ভিত করে দেবার মতন কেননা সাহিত্যিক হিসেবে কলকাতায় আমাকে বড়ো একটা পছন্দ করা হতো না আর একজন যুবক কিনা বহুদূর থেকে এসেছেন আমার লেখা নিতে আর আমাকে নিয়ে ক্রোড়পত্র প্রকাশ করার প্রস্তাব নিয়ে । সেই থেকে এবাদুলের সঙ্গে আমার আলাপ । এবাদুল আমার দুটি বই প্রকাশ করেছিলেন, একটি ছোটোগল্পের, “অতিবাস্তব গল্পগাছা” নামে এবং আরেকটি “হাংরি ইশতাহার সংকলন” । আমার লেখালিখি নিয়ে বহুকাল আগে সেই প্রথম ক্রোড়পত্র প্রকাশের পর নভেম্বর ২০১৯ সালে ৪১ বর্ষ প্রথম সংখ্যায় আবার ক্রোড়পত্র প্রকাশ করেন ।
 মলয় রায়চৌধুরী | 122.179.172.247 | ২৪ আগস্ট ২০২১ ১৯:১৭734895
মলয় রায়চৌধুরী | 122.179.172.247 | ২৪ আগস্ট ২০২১ ১৯:১৭734895হাংরি ও পরাবাস্তববাদের অবনিবনার অহেতুক চর্চা
মলয় রায়চৌধুরী
এক
হাংরি আন্দোলনকারীদের অবনিবনা নিয়ে যতো খিল্লি হয় তা কিন্তু পরাবাস্তববাদীদের মাঝে অবনিবনা নিয়ে হয় না । অথচ পরাবাস্তববাদীদের পরস্পরের ঝগড়া কতোজনের সঙ্গে যে প্রত্যেকের হয়েছিল তার কোনও হিসেব নেই । ফিদেল কাস্ত্রোর সঙ্গে চে গ্বেভারার অবনিবনা চেপে গিয়ে পালা করে ওই দুজনের টি শার্ট পরে ঘুরে বেড়ান বাঙালি ছোকরা লেখক-কবি। অথচ হাংরি আন্দোলনের আলোচনা শুরু করলেই সবাই তাঁদের পারস্পরিক অবনিবনা চর্চা করেন ; লেখালিখি বিশ্লেষণের কথা চিন্তা করেন না বা করতে চান না, বিশেষ করে বাঙালি আলোচকরা । নন্দিনী ধর হাংরি আন্দোলন আলোচনা করতে বসে দুম করে লিখে দিলেন যে আমার সংকলিত বই থেকে শৈলেশ্বর ঘোষকে বাদ দিয়েছি ; অথচ আমি হাংরি আন্দোলনকারীদের রচনার কোনো সংকলন প্রকাশ করিনি । নন্দিনী ধর লিখেছেন যে হাংরি আন্দোলনকারীরা নিজেদের ছোটোলোক ঘোষণা করে বিবিক্ততাকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন ; উনি জানতেন না যে আমি পাটনায় ইমলিতলা নামে এক অন্ত্যজ অধ্যুষিত বস্তিতে থাকতুম, অবনী ধর ছিলেন জাহাজের খালাসি আর পরে ঠেলাগাড়িতে করে কয়লা বেচতেন, শৈলেশ্বর ঘোষ আর সুভাষ ঘোষ এসেছিলেন উদ্বাস্তু পরিবার থেকে, দেবী রায় চায়ের ঠেকে চা বিলি করতেন । এ-থেকে টের পাওয়া যায় যে আলোচকরা কোনও বই পড়ার আগেই ভেবে নেন যে হাংরি আন্দোলনকারীদের রচনা আলোচনার সময়ে কী লিখবেন । হাংরি আন্দোলনকারীদের বিশ্ববীক্ষার তর্ক-বিতর্ক ও লেখালিখি বাদে দিয়ে আলোচকরা ব্যক্তিগত সম্পর্ককে গুরুত্ব দেন ।
অন্য বাঙালি লেখকদের ক্ষেত্রে কিন্তু তাঁরা এমন অডিটরসূলভ বিশ্লেষণ করতে বসেন না । বিদেশি সাহিত্যিকদের মাঝে নিজেদের বিশ্ববীক্ষার সমর্থনে পারস্পরিক বিবাদ-বিতর্কের কথা যেমন শোনা যায় তেমনটা বাঙালি লেখকদের ক্ষেত্রে বড়ো একটা দেখা যায় না । আমরা পড়েছি গোর ভিডাল আর নরম্যান মেইলারের বিবাদ এমনকি হাতাহাতি, সালমান রুশডি - জন আপডাইক বিবাদ, হেনরি জেমস - এইচ জি ওয়েল্স বিবাদ, জোসেফ কনরাড - ডি এইচ লরেন্স বিবাদ, জন কিটস - লর্ড বায়রন বিবাদ, চার্লস ডিকেন্স - হ্যান্স ক্রিশ্চিয়ান অ্যাণ্ডারসন বিবাদ ইত্যাদি । আলোচকরা কিন্তু তাঁদের রচনাবলী বিশ্লেষণের সময়ে সৃজনশীল কাজকেই গুরুত্ব দেন, বিবাদকে নয় ।
বাঙালি সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, মনে করেন মানুষ ও প্রাণীরা এসেছে অন্য গ্রহ থেকে, অনুকূল ঠাকুরের শিষ্য । ওই একই দপতরে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর পাশের কেবিনেই বসতেন ,যিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন না, ডারউইনের তত্বে বিশ্বাস করতেন, বামপন্হী ছিলেন । অথচ পরপস্পরের লেখা আলোচনার সময়ে এই বিষয়গুলো ওনাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যেত, যেন সাহিত্য আলোচনায় লেখকের বিশ্ববীক্ষার কোনো প্রভাব থাকে না । অধিকাংশ বাঙালি সাহিত্যিক এই ধরণের ভাই-ভাই ক্লাবের সদস্য । এদিকে হাংরি আন্দোলনকারীদের রচনা আলোচনা করতে বসে তাদের ব্যক্তিগত অবনিবনায় জোর দেন ।
এই তো সেদিন ক্লিন্টন বি সিলির জীবনানন্দ বিষয়ক গ্রন্হ ‘এ পোয়েট অ্যাপার্ট, পড়ার সময়ে হাংরি আন্দোলনকারীরা খালাসিটোলায় জীবনানন্দের যে জন্মদিন পালন করেছিল, তার বর্ণনা পড়ছিলুম । উনি ‘দি স্টেটসম্যান’ পত্রিকায় ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৮ তারিখে প্রকাশিত সংবাদ তুলে দিয়ে পরবর্তী প্রজন্মে জীবনানন্দের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেছেন । একই খবর প্রকাশিত হয়েছিল তখনকার সাপ্তাহিক ‘অমৃত’ পত্রিকায় । সেদিন সন্ধ্যায় জীবনানন্দ দাশের জন্মদিন পালনের জন্য টেবিলে উঠে পড়লেন হাংরি আন্দোলনের গল্পকার অবনী ধর আর নাচের সঙ্গে গাইতে লাগলেন একটা গান, যা তিনি জাহাজে খালসির কাজ করার সময়ে গাইতেন, বিদেশি খালাসিদের সঙ্গে । উপস্হিত সবাই, এমনকি হাংরি আন্দোলনের কয়েকজন ভেবেছিলেন গানটা আবোল-তাবোল, কেননা ইংরেজিতে তো এমনতর শব্দ তাঁদের জানা ছিল না । যে সাংবাদিকরা খবর কভার করতে এসেছিলেন তাঁরাও গানটাকে ভেবেছিলেন হাংরি আন্দোলনকারীদের বজ্জাতি, প্রচার পাবার ধান্দা । ‘অমৃত’ পত্রিকায় ‘লস্ট জেনারেশন’ শিরোনামে ঠাট্টা করে দুই পাতা চুটকি লেখা হয়েছিল, অবনী ধরের কার্টুনের সঙ্গে । ‘অমৃত’ পত্রিকায় ‘লস্ট জেনারেশন’ তকমাটি যিনি ব্যবহার করেছিলেন তিনি জানতেন না যে এই শব্দবন্ধ তৈরি করেছিলেন গারট্রুড স্টিন এবং বিশ শতকের বিশের দশকে প্যারিসে আশ্রয় নেয়া আর্নেস্ট হেমিংওয়ে, এফ স্কট ফিটজেরাল্ড, টি. এস. এলিয়ট, জন ডস প্যাসস, ই ই কামিংস, আর্চিবল্ড ম্যাকলিশ, হার্ট ক্রেন প্রমুখকে বলা হয়েছিল ‘লস্ট জেনারেশন’-এর সদস্য । অবনী ধর-এর নামের সঙ্গে অনেকেই পরিচিত নন । যাঁরা তাঁর নাম শোনেননি এবং ওনার একমাত্র বই ‘ওয়ান শট’ পড়েননি, তাঁদের জানাই যে ছোটোগল্পের সংজ্ঞাকে মান্যতা দিলে বলতে হয় যে অবনী ধর ছিলেন হাংরি আন্দোলনের সর্বশ্রেষ্ঠ ছোটো গল্পকার ।
গানটা এরকম, মোৎসার্টের একটা বিশেষ সুরে গাওয়া হয়:
জিং গ্যাং গুলি গুলি গুলি গুলি ওয়াচা,
জিং গ্যাং গু, জিং গ্যাং গু ।
জিং গ্যাং গুলি গুলি গুলি গুলি ওয়াচা,
জিং গ্যাং গু, জিং গ্যাং গু ।
হায়লা, ওহ হায়লা শায়লা, হায়লা শায়লা, শায়লা উউউউউহ,
হায়লা, ওহ হায়লা শায়লা, হায়লা শায়লা, শায়লা, উহ
শ্যালি ওয়ালি, শ্যালি ওয়ালি, শ্যালি ওয়ালি, শ্যালি ওয়ালি ।
উউউমপাহ, উউউমপাহ, উউউমপাহ, উউউমপাহ ।
১৯২০ সালে,, প্রথম বিশ্ব স্কাউট জাম্বোরির জন্য, রবার্ট ব্যাডেন-পাওয়েল, প্রথম বারন ব্যাডেন-পাওয়েল (স্কাউটিংয়ের প্রতিষ্ঠাতা) সিদ্ধান্ত নেন যে একটা মজার গান পেলে ভালো হয়, যা সব দেশের স্কাউটরা গাইতে পারবে ; কারোরই কঠিন মনে হবে না । উনি মোৎসার্টের এক নম্বর সিম্ফনির ইবি মেজরে বাঁধা সুরটি ধার করেছিলেন । গানটা স্কাউটদের মধ্যে তো বটেই সাধারণ স্কুল ছাত্রদের মধ্যেও জনপ্রিয় হয়েছিল । এই স্কাউটদের কেউ-কেউ জাহাজে চাকরি নিয়ে খালাসি এবং অন্যান্য কর্মীদের মধ্যে এটাকে ছড়িয়ে দিতে সফল হন । অবনী ধর বেশ কিছুকাল জাহাজে খালাসির কাজ করেছিলেন এবং তাঁরও ভালো লেগে যায় সমবেতভাবে গাওয়া গানটি । শতভিষা, কৃত্তিবাস, কবিতা, ধ্রুপদি পত্রিকার কর্নধারদের প্রিয় সঙ্গীত-জগত থেকে একশো আশি ডিগ্রি ঘুরে যাওয়া এই গান সেসময়ে নিতে পারেননি সাংবাদিক আর বিদ্যায়তনিক আলোচকরা, তার ওপর যেহেতু হাংরি আন্দোলনের ব্যাপার, তাই তাঁরা এটাকে অশিক্ষিত নেশাখোর-মাতালদের কারবার ভেবে হেঁ-হেঁ করে হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন ।
দুই
উত্তরবঙ্গে হাংরি জেনারেশনের প্রসার সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে, হাংরি পত্রিকা ‘কনসেনট্রেশন ক্যাম্প’ এর সম্পাদক অলোক গোস্বামী এই কথাগুলো লিখেছিলেন, তা থেকে অবনিবনার যৎসামান্য আইডিয়া হবে, আর এই অবনিবনার সঙ্গে পরাবাস্তববাদীদের নিজেদের অবনিবনারে যথেষ্ট মিল আছে :-
“নব্বুই দশকে সদ্য প্রকাশিত কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প বগলে নিয়ে এক ঠা ঠা দুপুরে আমি হাজির হয়েছিলাম শৈলেশ্বরের বাড়ির গেটে। একা। ইচ্ছে ছিল শৈলেশ্বরের সঙ্গে মুখোমুখি বসে যাবতীয় ভুল বোঝাবুঝি নিয়ে খোলাখুলি কথা বলবো। যেহেতু স্মরণে ছিল শৈলেশ্বরের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের স্মৃতি তাই আস্থা ছিল শৈলেশ্বরের প্রজ্ঞা,ব্যক্তিত্ব,যুক্তিবোধ তথা ভদ্রতাবোধের ওপর। দৃঢ় বিশ্বাস ছিল শৈলেশ্বর আমাদের ভুলগুলো ধরিয়ে দেবেন এবং যৌথ আলোচনাই পারবে সব ভুল বোঝাবুঝি মিটিয়ে নতুন উদ্যমে একসাথে পথ চলা শুরু করতে। কিন্তু দুভার্গ্য বশতঃ তেমন কিছু ঘটলো না। বেল বাজাতেই গেটের ওপারে শৈলেশ্বর। আমাকে দেখেই ভ্রূ কুঁচকে ফেললেন।
--কী চাই!
মিনমিন করে বললাম, আপনার সঙ্গে কথা বলবো।
--কে আপনি?
এক এবং দুই নম্বর প্রশ্নের ভুল অবস্থান দেখে হাসি পাওয়া সত্বেও চেপে গিয়ে নাম বললাম।
--কি কথা?
--গেটটা না খুললে কথা বলি কিভাবে!
--কোনো কথার প্রয়োজন নেই। চলে যান।
--এভাবে কথা বলছেন কেন?
--যা বলছি ঠিক বলছি। যান। নাহলে কিন্তু প্রতিবেশীদের ডাকতে বাধ্য হবো।
এরপর স্বাভাবিক কারণেই খানিকটা ভয় পেয়েছিলাম কারণ আমার চেহারাটা যেরকম তাতে শৈলেশ্বর যদি একবার ডাকাত, ডাকাত বলে চেঁচিয়ে ওঠেন তাহলে হয়ত জান নিয়ে ফেরার সুযোগ পাবো না। তবে 'ছেলেধরা' বলে চেল্লালে ভয় পেতাম না। সমকামিতার দোষ না থাকায় নির্ঘাত রুখে দাঁড়াতাম।
ভয় পাচ্ছি অথচ চলেও যেতে পারছি না। সিদ্ধান্তে পৌঁছতে গেলে আরও খানিকটা জানা বোঝা জরুরি।
--ঠিক আছে, চলে যাচ্ছি। তবে পত্রিকার নতুন সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে সেটা রাখুন।
এগিয়ে আসতে গিয়েও থমকে দাঁড়ালেন শৈলেশ্বর।
--কোন পত্রিকা?
--কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প।
--নেব না। যান।
এরপর আর দাঁড়াইনি। দাঁড়ানোর প্রয়োজনও ছিল না। ততক্ষণে বুঝে ফেলেছি ব্যক্তি শৈলেশ্বর ঘোষকে চিনতে ভুল হয়নি আমাদের। আর এই সমঝদারি এতটাই তৃপ্তি দিয়েছিল যে অপমানবোধ স্পর্শ করারই সুযোগ পায়নি।”
পরাবাস্তববাদীদের মতনই, শৈলেশ্বর ঘোষের হয়তো মনে হয়েছিল যে কলকাতায় তিনি হাংরি আন্দোলনের যে কেন্দ্র গড়ে তুলতে চাইছেন তাতে ফাটল ধরাবার চেষ্টা করা হচ্ছে । তাঁর আচরণ ছিল হুবহু আঁদ্রে ব্রেতঁর মতন । পরাবাস্তববাদ আন্দোলনে আঁদ্রে ব্রেতঁর সঙ্গে অনেকের সম্পর্ক ভালো ছিল না, দল বহুবার ভাগাভাগি হয়েছিল, অথচ সেসব নিয়ে বাঙালি আলোচকরা তেমন উৎসাহিত নন, যতোটা হাংরি আন্দোলনের দল-ভাগাভাগি নিয়ে। ইংরেজিতে মৈত্রেয়ী ভট্টাচার্য চৌধুরী হাংরি আন্দোলন নিয়ে ‘দি হাংরিয়ালিস্টস’ নামে একটি বই লিখেছেন, পেঙ্গুইন র্যাণ্ডাম হাউস থেকে প্রকাশিত । সেই বইটি বাংলা পত্রপত্রিকায় আলোচিত হল না ।
তিন
আনন্দবাজার পত্রিকায় ১৬ জুন ২০১৩ তারিখে গৌতম চক্রবর্তী হাংরি আন্দোলন সম্পর্কে এই কথাগুলো লিখেছিলেন ; তাতেও রয়েছে টিটকিরি, যা তিনি পরাবাস্তববাদীদের সম্পর্কে কখনও বলেছেন কিনা জানি না । উনি লিখেছিলেন :
“মানুষ, ঈশ্বর, গণতন্ত্র ও বিজ্ঞান পরাজিত হয়ে গেছে। কবিতা এখন একমাত্র আশ্রয়।... এখন কবিতা রচিত হয় অর্গ্যাজমের মতো স্বতঃস্ফূর্তিতে।
১৯৬২ সালে এই ভাষাতেই কলেজ স্ট্রিট কফি হাউস থেকে খালাসিটোলা, বারদুয়ারি অবধি সর্বত্র গোপন বিপ্লবী আন্দোলনের ব্লু প্রিন্টের মতো ছড়িয়ে পড়ে একটি ম্যানিফেস্টো। ২৬৯ নেতাজি সুভাষ রোড, হাওড়া থেকে প্রকাশিত এই ম্যানিফেস্টোর ওপরে লেখা ‘হাংরি জেনারেশন’। নীচের লাইনে তিনটি নাম। ‘স্রষ্টা: মলয় রায়চৌধুরী। নেতৃত্ব: শক্তি চট্টোপাধ্যায়। সম্পাদনা: দেবী রায়।’
তখনও কলেজ স্ট্রিটের বাতাসে আসেনি বারুদের গন্ধ, দেওয়ালে লেখা হয়নি ‘সত্তরের দশক মুক্তির দশক’। কিন্তু পঞ্চাশ পেরিয়ে-যাওয়া এই ম্যানিফেস্টোর গুরুত্ব অন্যত্র। এর আগে ‘ভারতী’, ‘কবিতা’, ‘কৃত্তিবাস’, ‘শতভিষা’ অনেক কবিতার কাগজ ছিল, সেগুলি ঘিরে কবিরা সংঘবদ্ধও হতেন। কিন্তু এই ভাবে সাইক্লোস্টাইল-করা ম্যানিফেস্টো আগে কখনও ছড়ায়নি বাংলা কবিতা।
ওটি হাংরি আন্দোলনের দ্বিতীয় ম্যানিফেস্টো। প্রথম ম্যানিফেস্টোটি বেরিয়েছিল তার কয়েক মাস আগে, ১৯৬১ সালের নভেম্বর মাসে। ইংরেজিতে লেখা সেই ম্যানিফেস্টো জানায়, কবিতা সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যায় না, বিভ্রমের বাগানে পুনরায় বৃক্ষরোপণ করে না। ‘Poetry is no more a civilizing manoeuvre, a replanting of bamboozled gardens.’ বিশ্বায়নের ঢের আগে ইংরেজি ভাষাতেই প্রথম ম্যানিফেস্টো লিখেছিলেন হাংরি কবিরা। কারণ, পটনার বাসিন্দা মলয় রায়চৌধুরী ম্যানিফেস্টোটি লিখেছিলেন। পটনায় বাংলা ছাপাখানা ছিল না, ফলে ইংরেজি।
দুটি ম্যানিফেস্টোতেই শেষ হল না ইতিহাস। হাংরি আসলে সেই আন্দোলন, যার কোনও কেন্দ্র নেই। ফলে শহরে, মফস্সলে যে কোনও কবিই বের করতে পারেন তাঁর বুলেটিন। ১৯৬৮ সালে শৈলেশ্বর ঘোষ তাঁর ‘মুক্ত কবিতার ইসতাহার’-এ ছাপিয়ে দিলেন ‘সমস্ত ভন্ডামির চেহারা মেলে ধরা’, ‘শিল্প নামক তথাকথিত ভূষিমালে বিশ্বাস না করা’, ‘প্রতিষ্ঠানকে ঘৃণা করা’, ‘সভ্যতার নোনা পলেস্তারা মুখ থেকে তুলে ফেলা’ ইত্যাদি ২৮টি প্রতিজ্ঞা। পরে বন্ধুদের মধ্যে ঝগড়া বাধবে। মলয় ব্যাংকের চাকরি নিয়ে বাইরে চলে যাবেন। শৈলেশ্বর, সুবো আচার্য এবং প্রদীপ চৌধুরীরা বলবেন, ‘মলয় বুর্জোয়া সুখ ও সিকিয়োরিটির লোভে আন্দোলন ছেড়ে চলে গিয়েছে।’কী রকম লিখতেন হাংরিরা? বছর দুয়েক আগে সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের ‘বাইশে শ্রাবণ’ ছবিতে গৌতম ঘোষের চরিত্রটি লেখা হয়েছিল হাংরি কবিদের আদলে।
‘জেগে ওঠে পুরুষাঙ্গ নেশার জন্য হাড় মাস রক্ত ঘিলু শুরু করে কান্নাকাটি
মনের বৃন্দাবনে পাড়াতুতো দিদি বোন বউদিদের সঙ্গে শুরু হয় পরকীয়া প্রেম’,
লিখেছিলেন অকালপ্রয়াত ফালগুনী রায়। র্যাঁবো, উইলিয়াম বারোজ এবং হেনরি মিলারের উদাহরণ বারে বারেই টেনেছেন হাংরিরা। ঘটনা, এঁরা যত না ভাল কবিতা লিখেছেন, তার চেয়েও বেশি ঝগড়া করেছেন। এবং তার চেয়েও বেশি বার গাঁজা, এলএসডি, মেস্কালিন আর অ্যাম্ফিটোমাইন ট্রিপে গিয়েছেন।
অতএব, সাররিয়ালিজ্ম বা অন্য শিল্প আন্দোলনের মতো বাঙালি কবিদের ম্যানিফেস্টোটি কোনও দিন গুরুত্বপূর্ণ হয়নি। কিন্তু ‘হাংরি’রা আজও মিথ। এক সময় ‘মুখোশ খুলে ফেলুন’ বলে তৎকালীন মন্ত্রী, আমলা, সম্পাদকদের বাড়িতে ডাকযোগে তাঁরা মুখোশ পাঠিয়ে দিয়েছেন। আবার এক সময় ‘প্রচন্ড বৈদ্যুতিক ছুতার’ কবিতাটি লেখার জন্য অশ্লীলতার মামলা হল মলয় রায়চৌধুরীর বিরুদ্ধে। উৎপলকুমার বসু, সুবিমল বসাকের বিরুদ্ধে জারি হল গ্রেফতারি পরোয়ানা।
রাষ্ট্র ও আদালত কী ভাবে কবিতাকে দেখে, সেই প্রতর্কে ঢুকতে হলে ১৯৬৫ সালে মলয় রায়চৌধুরীর বিরুদ্ধে মামলাটি সম্পর্কে জানা জরুরি। শক্তি চট্টোপাধ্যায় কাঠগড়ায় উঠেছেন মলয়ের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে। পাবলিক প্রসিকিউটরের জিজ্ঞাসা, ‘প্রচন্ড বৈদ্যুতিক ছুতার’ কবিতাটা পড়ে আপনার কী মনে হয়েছে?
শক্তি: ভাল লাগেনি।
প্রসিকিউটর: অবসিন কি? ভাল লাগেনি বলতে আপনি কী বোঝাতে চাইছেন?
শক্তি: ভাল লাগেনি মানে জাস্ট ভাল লাগেনি। কোনও কবিতা পড়তে ভাল লাগে, আবার কোনওটা ভাল লাগে না।
শক্তি সাক্ষ্য দিয়েছিলেন মলয়ের বিরুদ্ধে। কয়েক মাস পরে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় মলয়ের সমর্থনে...
প্রসিকিউটর: কবিতাটা কি অশ্লীল মনে হচ্ছে?
সুনীল: কই, না তো। আমার তো বেশ ভাল লাগছে। বেশ ভাল লিখেছে।
প্রসিকিউটর: আপনার শরীরে বা মনে খারাপ কিছু ঘটছে?
সুনীল: না, তা কেন হবে? কবিতা পড়লে সে সব কিছু হয় না।
একই মামলায় শক্তি ও সুনীল পরস্পরের বিরুদ্ধে। তার চেয়েও বড় কথা, ’৬৫ সালে এই সাক্ষ্য দেওয়ার আগের বছরই সুনীল আইওয়া থেকে মলয়কে বেশ কড়া একটি চিঠি দিয়েছিলেন, ‘লেখার বদলে আন্দোলন ও হাঙ্গামা করার দিকেই তোমার ঝোঁক বেশি। রাত্রে তোমার ঘুম হয় তো? মনে হয়, খুব একটা শর্টকাট খ্যাতি পাবার লোভ তোমার।’ ব্যক্তিগত চিঠিতে অনুজপ্রতিম মলয়কে ধমকাচ্ছেন, কিন্তু আদালতে তাঁর পাশে গিয়েই দাঁড়াচ্ছেন। সম্ভবত, বন্ধু-শত্রু নির্বিশেষে অনুজ কবিদের কাছে সুনীলের ‘সুনীলদা’ হয়ে ওঠা হাংরি মামলা থেকেই। প্রবাদপ্রতিম কৃত্তিবাসী বন্ধুত্বের নীচে যে কত চোরাবালি ছিল, তা বোঝা যায় উৎপলকুমার বসুকে লেখা সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের একটি চিঠি থেকে, ‘প্রিয় উৎপল, একদিন আসুন।...আপনি তো আর শক্তির মতো ধান্দায় ঘোরেন না।’
তা হলে কি হাংরি আন্দোলন বাংলা সাহিত্যে প্রভাবহীন, শুধুই কেচ্ছাদার জমজমাট এক পাদটীকা? দুটি কথা। হাংরিদের প্রভাবেই কবিতা-সংক্রান্ত লিট্ল ম্যাগগুলির ‘কৃত্তিবাস’, ‘শতভিষা’ গোছের নাম বদলে যায়। আসে ‘ক্ষুধার্ত’, ‘জেব্রা’, ‘ফুঃ’-এর মতো কাগজ। সেখানে কবিতায় বাঁকাচোরা ইটালিক্স, মোটাদাগের বোল্ড ইত্যাদি হরেক রকমের টাইপোগ্রাফি ব্যবহৃত হত। পরবর্তী কালে সুবিমল মিশ্রের মতো অনেকেই নিজেকে হাংরি বলবেন না, বলবেন ‘শুধুই ছোট কাগজের লেখক’। কিন্তু তাঁদের গল্প, উপন্যাসেও আসবে সেই টাইপোগ্রাফিক বিভিন্নতা। তৈরি হবে শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন। হাংরিরা না এলে কি নব্বইয়ের দশকেও হানা দিতেন পুরন্দর ভাট?
আসলে, ম্যানিফেস্টোর মধ্যেই ছিল মৃত্যুঘণ্টা। ’৬২ সালে হাংরিদের প্রথম বাংলা ম্যানিফেস্টোর শেষ লাইন, ‘কবিতা সতীর মতো চরিত্রহীনা, প্রিয়তমার মতো যোনিহীনা ও ঈশ্বরীর মতো অনুষ্মেষিণী।’ হাংরিরা নিজেদের যত না সাহিত্যবিপ্লবী মনে করেছেন, তার চেয়েও বেশি যৌনবিপ্লবী।”
চার
গৌতম চক্রবর্তী বহু বিদেশি নাম বাদ দিয়ে দিয়েছেন ; সম্ভবত তিনিও লেখার আগেই হাংরি আন্দোলনকারীদের ব্যঙ্গ করবেন বলে ঠিক করে ফেলেছিলেন । হাংরি আন্দোলনকারীরা জানতো যে ব্রিটিশ ঔপন্যাসিক চার্লস ডিকেন্স তিনি মর্গে যেতে ভালোবাসতেন; সেখানে দিনের একটা সময় কাটাতেন। মর্গে যাওয়া ছাড়াও চার্লস ডিকেন্সের ছিল আফিমে আসক্তি, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতন। আর্নেস্ট হেমিংওয়ের ছিল মদের প্রতি আসক্তি, কমলকুমার মজুমদারের মতন। মদের ভালোবাসা থেকে তিনি লিখেছেন- যখন আপনি মাতাল, তখন আপনি অনেক বেশি ভদ্র । এটা আপনার মুখ বন্ধ রাখতে সাহায্য করবে। আমেরিকান রোমান্টিক মুভমেন্টের প্রধান ব্যক্তি, অ্যাডগার অ্যালান পো ছিলেন মাদকাসক্ত। হেমিংওয়ের মতো তিনিও দুঃখ-কাতরতা থেকে মুক্ত থাকার জন্য মদ পান শুরু করেন। ব্রিটিশ কবি, রোমান্টিক মুভমেন্টের অন্যতম প্রবক্তা, কুবলা খান ও দ্য রাইম অব দ্য এনসিয়েন্ট মেরিনার এর কবি স্যমুয়েল টেইলর কোলরিজে আফিমে আসক্ত ছিলেন। সেই সময় তিনি আফিমখোর হিসেবে ব্রিটেনে পরিচিত ছিলেন এবং এটা নিয়ে তিনি গর্বও বোধ করতেন। তিনি বলেছেন, কুবলা খান লিখতে গিয়ে আফিমের ঘোর তাঁকে সাহায্য করেছিল। ট্রেজার আইল্যান্ড, দ্য স্ট্রেঞ্জ কেস অব ডা. জ্যাকেল অ্যান্ড মি. হাইড-এর স্রষ্টা স্কটিশ সাহিত্যিক রবার্ট লুইস স্টিভেনসন ছিলেন কোকেনে আসক্ত। তার স্ত্রীর ভাষ্যমতে, তিনি কোকেন নিয়ে করে মাত্র ছয় দিনে ঘোরগ্রস্ত অবস্থায় ৬০ হাজার শব্দ লিখেছিলেন। এর মধ্যে দ্য স্ট্রেঞ্জ কেস অব ডা. জ্যাকেল অ্যান্ড মি. হাইডও লিখেছেন।
.
তিন
১৯১৭ সালে গিয়ম অ্যাপলিনেয়ার “সুররিয়ালিজম” অভিধাটি তৈরি করেছিলেন, যার অর্থ ছিল বাস্তবের অতীত। শব্দটি প্রায় লুফে নেন আঁদ্রে ব্রেতঁ, নতুন একটি আন্দোলন আরম্ভ করার পরিকল্পনা নিয়ে, যে আন্দোলনটি হবে পূর্ববর্তী ডাডাবাদী আন্দোলন থেকে ভিন্ন । ত্রিস্তঁ জারা উদ্ভাবিত ডাডা আন্দোলন থেকে সরে আসার কারণ হল ব্রেতঁ সহ্য করতে পারতেন না ত্রিস্তঁ জারাকে, কেননা কবি-শিল্পী মহলে প্রতিশীল্পের জনক হিসাবে ত্রিস্তঁ জারা খ্যাতি পাচ্ছিলেন। আঁদ্রে ব্রেতঁ সুররিয়ালিজম তত্বটির একমাত্র ব্যাখ্যাকারী হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে আরম্ভ করেন। ১৯১৯ সালে ত্রিস্তঁ জারাকে কিন্তু ব্রেতঁ চিঠি লিখে প্যারিসে আসতে বলেছিলেন । একইভাবে ‘হাংরি’ শব্দটি মলয় রায়চৌধুরী পেয়েছিলেন কবি জিওফ্রে চসার থেকে । এই ‘হাংরি’ শব্দটি নেয়ার জন্য মলয় রায়চৌধুরীকে যেভাবে আক্রমণ করা হয়েছে, তেমন কিছুই করা হয়নি আঁদ্রে ব্রেতঁ ও ত্রিস্তঁ জারা সম্পর্কে । মলয় রায়চৌধুরী হাংরি জেনারেশন আন্দোলন ঘোষণা করেন ১৯৬৫ সালের পয়লা নভেম্বর একটি লিফলেট প্রকাশের মাধ্যমে ।
পরাবাস্তববাদী আন্দোলনে, প্রথম থেকেই, আঁদ্রে ব্রেতঁ’র সঙ্গে অনেক পরাবাস্তববাদীর সদ্ভাব ছিল না, কিন্তু পরাবাস্তববাদ বিশ্লেষণের সময়ে আলোচকরা তাকে বিশেষ গুরুত্ব দেন না । আমরা যদি বাঙালি আলোচকদের কথা চিন্তা করি, তাহলে দেখব যে তাঁরা হাংরি জেনারেশন বা ক্ষুধার্ত আন্দোলন বিশ্লেষণ করার সময়ে হাংরি জেনারেশনের সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে অত্যধিক চিন্তিত, হাংরি আন্দোলনকারীদের সাহিত্য অবদান নিয়ে নয় । ব্যাপারটা বিস্ময়কর নয় । তার কারণ অধিকাংশ আলোচক হাংরি জেনারেশনের সদস্যদের বইপত্র সহজে সংগ্রহ করতে পারেন না এবং দ্বিতীয়ত সাংবাদিক-আলোচকদের কুৎসাবিলাসী প্রবণতা ।
আঁদ্রে ব্রেতঁ তাঁর বন্ধু পল এলুয়ার, বেনিয়ামিন পেরে, মান রে, জাক বারোঁ, রেনে ক্রেভালl, রোবের দেসনস, গিয়র্গে লিমবোর, রোজের ভিত্রাক, জোসেফ দেলতিল, লুই আরাগঁ ও ফিলিপে সুপোকে নিয়ে ১৯১৯ পরাবাস্তববাদ আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন । কিছু
দুই
যাঁরা কবি ও লেখকদের পারস্পরিক অবনিবনাকে গুরুত্ব দিয়েছেন, তাঁরা লেখক-প্রতিস্ব নির্মাণের ব্যাপারটা ভেবে দ্যাখেননি, বিশেষ করে সমাজটির আর্থসামাজিক পৃষ্ঠপটে ও পূর্বের সাহিত্যিক পঠন-পাঠনের প্রভাবে নির্মিত প্রতিস্ব ।
প্রথম ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র ও প্রথম ছোটোগল্পকার পূর্নচন্দ্র থেকে হাল আমলের মফসসলের কথাসাহিত্যিক, প্রান্তিক ও শহুরে গল্পকার কিংবা মেট্রপলিটান ঔপন্যাসিক, তাঁদের লেখক প্রতিস্ব অবিনির্মাণ করলে প্রথম যে উপাদানটি পাওয়া যাবে, তা তাঁদের মাতৃভাষায় এবং অন্যান্য যে ভাষায় তাঁদের দখল আছে, সে ভাষায় পূর্ব প্রজন্মগুলোর সাহত্যিকদের লেখা গল্প-উপন্যাসের পঠন-পাঠনের জমা করা স্মৃতি । ব্যক্তিপ্রতিস্ব নির্মাণে ভাষার অবদান অনস্বীকার্য, কিন্তু লেখক-প্রতিস্ব নির্মাণে ভাষাসাহিত্যের জ্ঞান তথা সাহিত্যের বিশেষ ঝোঁকের প্রতি লেখকের টান, তাঁর লেখনকর্মের আদল আদরা দিশা তাৎপর্য অন্তর্নিহিত-সম্পদ দাপট চৈতন্য অস্তিত্ব আত্ম-উন্মোচন এমনকী তাঁর সাহিত্য চক্রান্তক কলমটির গঠনকারী মূল উপাদান । তাঁদের লেখন-অভিজ্ঞতার মালিকানার বখরা কিন্তু তাঁদের পড়া পূর্বসূরী গল্পকার-ঔপন্যাসিক-দার্শনিকদের প্রাপ্য।
আমি যে প্রতিস্ব-নির্মাণের কথা বলছি তা বাংলা সাহিত্যের এক বিশেষ বাঁকবদলের সময়কার । উল্লেখ্য যে ভারতবর্ষে পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, বেতাল পঞ্চবিংশতি, কথাসরিৎসাগর, বৃহৎকথা, কথামঞ্জরী, দশকুমার চরিত, বাদবদত্তা ইত্যাদি গদ্যে রচিত কথাবস্তুর অতিপ্রাচীন ঐতিহ্য আছে । ইংরেজরা আসার পর, এবং ফলে, বাংলা গদ্যসাহিত্য ও গদ্যে নানা ধরণের সংরূপের উদ্ভব জলবিভাজকের কাজ করেছিল ; আমি সেদিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি । এক নতুন নন্দনক্ষেত্র তৈরি হয়েছিল সাহিত্যের এলাকায়, যে এলাকায় লেখক নামের নির্মিত-প্রতিস্বের মানুষটির লেখনকর্মকে কৌমনিরপেক্ষ ব্যক্তিলক্ষণ হিসেবে নৈতিকতা আর বৈধতা আরোপের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছিল । ফলে লেখনকর্ম বা পাঠবস্তুতে সতত কেন্দ্র দখল করে থাকলেন লেখ-সৃষ্টিকারী ব্যক্তিমালিকটি ।
ইংরেজরা আসার পরই, আর বাংলা কথাসাহিত্যের শুরুতেই যে লেখকরা নির্মিত-প্রতিস্ব নিয়ে লেখন-পরিসরে নেমেছিলেন, তা কিন্তু নয়। লেখন পরিসরে ব্যক্তিনামের লালন, ব্যক্তি-আধিপত্যের ছাপ, ব্যক্তিপ্রসূত রচনাগত মৌলিকতা, ব্যক্তিসৃজনশীলতা ইত্যাদি প্রতর্কগুলো হিন্দু বাঙালির জীবনে প্রবেশ করতে পেরেছিল সেই সময়কার কলকাতায় ইউরোপীয় আলোকপ্রাপ্তির মননবিশ্বটি পাকাপাকি ভাবে থিতু হয়ে বসার পর । ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা, ১৮৩৫ থেকে শিক্ষার বাহন হিসেবে ইংরেজি, তারপর ১৮৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিক্ষিত বাঙালির সমাজে ওই মননবিশ্ব প্রবেশ করতে পেরেছিল। বাংলা ভাষার প্রথম উপন্যাস ‘দুর্গেশনন্দিনী’ প্রকাশিত হয় ১৮৬৫ সালে, লেখক হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্রের মননবিশ্বটি ওই আদরায় নির্মিত হবার পর এবং ফলে, আর একই কারণে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাই পূর্ণচন্দ্র দ্বারা রচিত হলো, ১৮৭৩ সালে, প্রথম বাংলা ছোটোগল্প ‘মধুমতী’ । তার আগে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা এবং ১৮৩১ সালে প্রকাশিত ‘নববাবুবিলাস’ আর ১৮৫৮ সালে প্রকাশিত প্যারীচাঁদ মিত্রের লেখা ‘আলালের ঘরের দুলাল’ পাঠবস্তুগুলোতে ওই মননবিশ্বের ছাপ ছিল না ।
পূর্ণচন্দ্র তাঁর গল্পটিতে নামস্বাক্ষর করেননি । ‘নববাবুবিলাস’ আর ‘আলালের ঘরের দুলাল’ ছদ্মনামে লেখা । নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী তাঁর ‘বাংলা ছোটোগল্প — সংক্ষিপ্ত সমালোচনা’ বইতে জানিয়েছেন যে ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকার সময়কালে ( ১২৮০ থেকে ১৩০৬ বঙ্গাব্দ ) বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় একশ ছাব্বিশটি ছোটোগল্প প্রকাশিত হয়েছিল যেগুলোয় লেখকরা নামস্বাক্ষর করেননি, এমনকী ছদ্মনামও নয় । রচনার সঙ্গে লেখকের নাম দেওয়ার প্রথাটি প্রবর্তন করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রাহ্মধর্মের প্রভাবশালী প্রতিনিধি । সেসময়ে ব্রা্হ্মধর্ম হয়ে উঠেছিল ওই মননবিশ্বের ধারক ও বাহক । নামস্বাক্ষর না-করার প্রক্রিয়াটি থেকে স্পষ্ট যে কথাবস্তুর রচয়িতারা জানতেন না যে লেখকসত্তা বলে কোনো ব্যাপার হয়, এবং লেখকের নামটি সত্তাটিকে বহন করে । কোনও কথাবস্তু যে মেধাস্বত্ত, সে ধারণাটির প্রতিষ্ঠা হতে সময় লেগেছিল । তার কারণ অস্তিত্বের কেন্দ্রে ব্যক্তিমানুষকে স্হাপনের কর্মকাণ্ডটির প্রভাব, যাকে উনিশ শতকের রেনেসঁস বলা হয়, সেই চিন্তাচেতনাকে ছড়িয়ে দেবার জন্য অজস্র নির্মিত-প্রতিস্বের প্রয়োজন ছিল । ইউরোপীয় চিন্তনতন্ত্রটির বাইরে যে নন্দনক্ষেত্রটি রয়ে গেল, জলবিভাজিকার অন্য দিকে, তাকে বটতলা নামে এইজন্য দোষারোপ করা হল যে সেই এলাকায় ব্যক্তিএককগুলো অনির্মিত। জেমস লঙ বললেন বটতলার বইগুলো অশ্লীল ও অশোভন, যার দরুন বাংলার সংস্কৃতি থেকে লোপাট হয়ে গেল বইগুলো ।
ইউরোপ থেকে আনা সাহিত্য-সংরূপগুলোর সংজ্ঞার স্বামীত্ব, তাদের ব্যাখ্যা করার অধিকার, দেশীয়করণের বৈধতা, সেসব বিধিবিধান তত্বায়নের মালিকানা, কথাবস্তুটির উদ্দেশ্যমূলক স্বীকৃতি, চিন্তনতন্ত্রটির অন্তর্গত সংশ্লেষে স্বতঃঅনুমিত ছিল যে, অনির্মিত লেখকপ্রতিস্বের পক্ষে তা অসম্ভব, নিষিদ্ধ, অপ্রবেশ্য, অনধিকার চর্চা । ব্যাপারটা স্বাভাবিক, কেননা যাঁরা সংজ্ঞাগুলো সরবরাহ করছেন, তাঁরাই তো জানবেন যে সেসব সংজ্ঞার মধ্যে কী মালমশলা আছে, আর তলে-তলে কীইবা তাদের ধান্দা । ফলে, কোনও কথাবস্তু যে সংরূপহীন হতে পারে, লেখক-এককটি চিন্তনতন্ত্রে অনির্মিত হতে পারে, রচনাকার তাঁর পাঠবস্তুকে স্হানাংকমুক্ত সমাজপ্রক্রিয়া মনে করতে পারেন, বা নিজেকে বাংলা সাহিত্যের কালরেখার বাইরে মনে করতে পারেন, এই ধরণের ধারণাকে একেবারেই প্রশ্রয় দেয়নি ওই চিন্তনতন্ত্রটি । বর্তমান কালখণ্ডে, আমরা জানি, একজন লোক লেখেন তার কারণ তিনি ‘লেখক হতে চান’ । অথচ লেখক হতে চান না এরকম লোকও তো লেখালিখি করতে পারেন । তাঁরা সাহিত্যসেবক অর্থে লেখক নন, আবার সাহিত্যচর্চাকারী বিশেষ স্হানাংক নির্ণয়-প্রয়াসী না-লেখকও নন । তাঁদের মনে লেখক হওয়া-হওয়ি বলে কোনও সাহিত্য-প্রক্রিয়া থাকে না ।
বহুকাল যাবৎ বিভিন্ন আলোচককে মন্তব্য করতে দেখা গেছে যে, উপন্যাস আর্ট ফর্মটির বঙ্গীয়করণ করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, ছোটোগল্প আর্টফর্মটিকে সম্পূর্ণ দেশজ করে নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, সনেট-তের্জারিমা-ভিলানেলকে এতদ্দেশীয় করেছিলেন প্রমথ চৌধুরী ইত্যাদি । এই যে একটি ভিন্ন ভাষসাহিত্যের সংরূপকে আরেকটি ভাষাসাহিত্যে এনে সংস্হাপন, এর জন্য দ্বিভাষী দক্ষতা এবং সংরূপটি সম্পর্কে গভীর জ্ঞানই যথেষ্ট নয় । যিনি এই কাজটিতে লিপ্ত, তাঁর গ্রাহীক্ষমতা, বহনক্ষমতা ও প্রতিস্হাপন ক্ষমতা থাকা দরকার। অমন ক্ষমতা গড়ে ওঠে জ্ঞান আহরণের মাধ্যমে । আর এই জ্ঞান আহরণ তখনই সম্ভব যখন আ্হরণকারীর লেখক-প্রতিস্বের নির্মাণ ঘটে জ্ঞানটির পরিমণ্ডলে ।
অনির্মিত লেখক-একককে ব্র্যাণ্ডার ম্যাথিউজ প্রণীত ছোটোগল্পের সংজ্ঞার প্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করা যাক । ‘দি ফিলজফি অফ দি শর্ট স্টোরি’ বইতে ম্যাথিউজ বলেছেন, “যাহা কেবলমাত্র গল্প এবং পরিসরে ক্ষুদ্র, তাহাই ছোটোগল্প নহে । ভাবের ঐক্য ছোটোগল্পের পক্ষে অপরিহার্য এবং এইখানেই উপন্যাসের সহিত ইআর পপধান প্রভেদ । ছোটোগল্পে ভাবের ঐকভ আছে, উপন্যাসে নাই । ক্ল্যাসিকাল ফরাসি নাটকের তিনটি ঐক্যই ফরাসি নাটকে আছে ; ইহা একটি ক্ষেত্রে, একটি দিনে, বিশেষ একটি ঘটনা দেখায় । ছোটোগল্পে একটিমাত্র চরিত্র, ঘটনা বা ভাব থাকে, অথবা একটিমাত্র পরিস্হিতির পটভূমিকায় কতকগুলো ভাবের সমাবেশ ঘটে।” এখন, অনির্মিত লেখক-প্রতিস্বের কাছে ‘ভাবের ঐক্য’, ‘ভাবের সমাবেশ’ ‘ক্লসিকাল ফরাসি নাটক’ ইত্যাদি ভাবকল্পগুলো দুর্ভেদ্য থেকে যাবে, এবং ব্যাখ্যার পরও বিমূর্ততা কাটবে না ।
‘অ্যান ইনট্রোডাকশান টু দি স্টাডি অফ লিটারেচার’ বইতে দেয়া ডাবলু. এইচ. হাডসন-এর তৈরি অনুশাসনের প্রেক্ষিতেও ব্যাপারটা বিচার করা যেতে পারে । হাডসন বলেছেন, “ছোটোগল্পে শিল্পকলার মূল্য নির্ধারণের জন্য ‘একক উদ্দেশ্য ও ভাবের ঐক্য’ বজায় আছে কিনা তা দেখা উচিত।” এখানেও প্রশ্ন উঠবে ‘শিল্পকলা’, তার ‘মূল্য নির্ধারণ’ এবং ‘একক উদ্দেশ্য’ ভাবকল্পগুলো নিয়ে । বস্তুত যে চিন্তনতন্ত্রের কথা একটু আগে বলেছি, তার সরবরাহ করা সংজ্ঞায় খাপ খায়নি বলে পূর্ণচন্দ্র চট্টপাধ্যায়ের লেখা ‘মধুমতী’ রচনাটিকে সার্থক ছোটোগল্পের তকমা দেয়া হয়নি । সার্থক ছোটোগল্পের তকমা দেয়া হল ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের লেখা ‘দেনাপাওনা’ রচনাটিকে । ছোটোগল্পের সংজ্ঞাকে গভীরভাবে বুঝতে না পারলে ‘সার্থক’ ছোটোগল্প লেখা সম্ভব ছিল না । সার্থকতা নামের মানদন্ডটি ওই চিন্তনতন্ত্রের ফসল । বর্তমান কালখণ্ডে ওই চিন্তনতন্ত্র বাতিল হয়ে গেছে, সেটা ভিন্ন প্রসঙ্গ ।
ওপরের কথাগুলো এইজন্য বলতে হল যে অবনী ধর, যাঁর চোদ্দটি গদ্য নিয়ে ‘ওয়ান সট’ বইটি প্রকাশিত হয়েছিল, তিনি ছোটোগল্প-লেখক বা গল্পকার হওয়া-হওয়ি অবস্হান থেকে সেগুলো লেখেননি, এবং তাঁর লেখক-প্রতিস্বটি ছিল অনির্মিত । ১৯৬৯ থেকে ২০০৩ পর্যন্ত, এই কালখণ্ডে তিনি এও চোদ্দটি গদ্যই লিখেছিলেন। ১৯৭৫ সালের পর তিনি লেখালিখি ছেড়ে দিয়েছিলেন । হাংরি আন্দোলনের সময়ে তাঁর সঙ্গে আমার একবারই দেখা হয়েছিল, অশোকনগরে, কিন্তু তখনও তিনি লেখালিখি আরম্ভ করেননি, যদিও তিনি নিজের জীবনের এই ঘটনাগুলো শোনাতে ভালোবাসতেন । তাঁর কথনভঙ্গিমা ও জীবননাট্যের ঘটনা থেকে স্পষ্ট ছিল যে কথাবস্তুর পরিসরটি সেই সময়ের সাহিত্যিক ডিসকোর্স এবং কাউন্টার-ডিসকোর্স থেকে একেবারে আলাদা, এমনকী হাংরি আন্দোলনের গল্পকার-ঔপন্যাসিক থেকেও আলাদা । ১৯৯৪ সালে কলকাতায় ফিরে জানতে পারি যে অবনী ধরের রচনাগুলো নিয়ে বই বের করার উৎসাহ কোনও হাংরি আন্দোলনকারী দেখাননি । আমি শর্মী পাণ্ডেকে অনুরোধ করি যে অবনী ধরের গদ্যগুলো নিয়ে একটা সংগ্রহ ওদের শিলালিপী প্রকাশনী থেকে বের করতে । শর্মী আর ওর স্বামী শুভঙ্কর দাশ তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে যায় আর আমাকে একটা ভূমিকা লিখে দিতে বলে । এই সময়ে অবনী ধরের সঙ্গে আমার বেশ কয়েকবার সাক্ষাৎ ঘটে আর ওনার জীবন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে ফেলি । অবনী ধর জন্মেছিলেন ১৯৩৪ সালে, তখনকার পূর্ববঙ্গের মাদারিপুর জেলার কালাকিনি থানার পাঙাশিয়া গ্রামে. তাঁর মামার বাড়িতে । মারা যান ২০০৭ সালে, অশোকনগরে । তাঁর বাবা বঙ্কিমচন্দ্র ধর ( ১৯০৫ ) ওই জেলার মাইচপাড়া গ্রামের নিবাসী ছিলেন, সাত ভাইয়ের সবচেয়ে ছোট ; বঙ্কিমচন্দ্র ম্যাট্রিক পাশ করেছিলেন, কিন্তু কখনও কোনও চাকরি বা ব্যবসা করেননি ; স্বাদেশী আন্দোলনে যোগ দেবার কারণে কয়েকমাসের জেল হয়েছিল তাঁর । বঙ্কিমচন্দ্র তখনকার দিনের ম্যাট্রিক পাশ ছিলেন, অর্থাৎ যে চিন্তনতন্ত্রের কথা একটু আগে বলেছি, তার মননবিশ্বে অবনী ধরের প্রতিস্বনির্মাণের সুযোগটি গড়ে ওঠার সম্ভাবনা ছিল, বিশেষ করে অবনী ধর যখন তাঁর বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান ।
অবনী ধরের বয়স যখন এক বছর, তখন তাঁর বাবা বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে, তাঁর মা লাবণ্য ধর ( ১৯১৫ – ১৯৭৭ ) , আর ঠাকুমাকে নিজেদের ভাগ্যের ওপরে ছেড়ে দিয়ে, অন্য এক তরুণীর সঙ্গে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, এবং বাকি জীবন বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর সঙ্গিনী বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীরূপে ভিক্ষা করে চালিয়েছিলেন । যদিও বঙ্কিমচন্দ্র মারা যান ১৯৬২ সালে, তাঁর মৃত্যুর খবর অবনীরা পান ১৯৭২ সালে । ততোদিন তাঁর মা শাঁখা-সিঁদুর পরতেন । অবনী ধরের লেখক-প্রতিস্ব প্রাগুক্ত চিন্তনতন্ত্রের পরিসরে যদি গড়ে উঠত, তাহলে তিনি এই ট্র্যাজেডির মুহূর্তটি নিয়ে একটি কথাবস্তু তৈরি করতে পারতেন, কেননা ইউরোপীয় সাহিত্যে গ্রিসের সময় থেকে ব্যক্তি-এককের ট্র্যাজেডিটি লেখকত্ব প্রতিষ্ঠার অন্যতম উপাদান ছিল, যা খ্রিস্টের নৃশংস হত্যা ও আত্মবলিদানের প্রতীকি অতিকথার প্রচার-প্রসারের কারণে সাহিত্যের নন্দনক্ষেত্রটিকে দখল করে নিতে পেরেছিল । তাছাড়া বাইবেলোক্ত “আরিজিনাল সিন” বা প্রথম পাপের পতনযন্ত্রণাকে সর্বজনীন নৈতিক-দার্শনিক বনেদে পালটে ফেলার জন্যেও জরুরি ছিল ইউরোপীয় সাহিত্যের পাতায় পাতায় ব্যক্তি-ট্র্যাজেডির উপস্হিতি ।
অবনী ধরের জীবনে বহুবার বহুরকম ট্র্যাজেডি সংঘটন দেখা গেছে, কিন্তু সেসব অভিজ্ঞতার সরাসরি মালিকানা সত্তেও তিনি সংঘটন-মুহূর্ত বা ক্লাইম্যক্স বা হুইপক্র্যাক এনডিং প্রয়োগ করে কথাবস্তুকে ঔপনিবেশিক সাহিত্য-অনুশাসন ও হেলেনিক মূল্যবোধের অন্তর্ভুক্ত করেননি । প্রকৃত প্রস্তাবে কথাবস্তুগুলো গড়ে উঠেছে ঔপনিবেশিক সাহিত্য-মূল্যবোধের আওতার বাইরে । প্রসঙ্গত, যে সময়ে অবনী ধর তাঁর প্রথম পর্বের গদ্যগুলো লিখেছিলেন, সেসময়ে মান্যতাপ্রাপ্ত বাংলা ছোটো গল্পকাররা ইউরোপীয় সাহিত্যের অনুশাসন মোতাবেক, বিষণ্ণতা, পারক্য, প্রেমের বিকার, মৃত্যুপ্রবণতা, নিঃসঙ্গতার বেদনা,শহুরে যৌনতা ইত্যাদির চর্চা করছিলেন ।
বাবা বঙ্কিমচন্দ্র তাঁদের একা ফেলে নিরুদ্দেশ হবার কারণে বছর পাঁচেক অন্নকষ্টে ভোগার পর তখনকার বিহারে ( এখন ঝাড়খণ্ড ) মধুপুরনিবাসী অবনীর ‘বুড়োমা’ অর্থাৎ তাঁর ঠাকুর্দার ভাইয়ের স্ত্রী, অবনী ও তাঁর মাকে দেখাসোনার জন্য, ও নিজের বার্ধক্যে দেখভালের জন্য, সেখানে নিয়ে গেলেন । যদিও অবনীর জ্যাঠামশাবরা, প্রথম দুজন ডাক্তার, ততীয়জন উকিল, চতুর্থজন স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন, এবং পঞ্চম ও ষষ্ঠ যথাক্রমে দেওঘর ও মধুপুরে আশ্রম বসিয়ে তার মোহন্ত ছিলেন, অবনীর পড়াশুনার এবং স্কুলে ভর্তি হবার সুরাহা হলো না । বুড়োমার আশ্রয়ে অবনী ও তাঁর মায়ের অন্ন সমস্যার সমাধান হলেও, শিক্ষাপ্রাপ্তির সুযোগ ঘটল না । স্কুলে ভর্তির জন্য অবনীকে কলকাতার চেতলায় মামারবাড়ি যেতে হলো । প্রবাদবাক্যের মামার বাড়ির আবদারের বদলে অহরহ দুর্ব্যাবহার জোটায়, ১৯৫০ সালের পয়লা অক্টোবর, কাউকে না জানিয়ে, স্কুল থেকে পালিয়ে, অবনী চলে গেলেন মার্চেন্ট নেভিতে, খালাসির কাজ নিয়ে । তখন তাঁর ষোলো বছর বয়স ।
এই সময়ের অভিজ্ঞতাগুলো অবনী সংগ্রহ করেন জাহাজে খালাসির কাজ করার সময়ে, বিভিন্ন দেশের বন্দর-শহরে, ইউরোপ তখনও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভাঙন কাটিয়ে উঠতে পারেনি । বস্তুত তাঁর খালাসিপর্বের কথাবস্তুগুলো, কথনভঙ্গীর অন্তর্গত আহ্লাদময়তার কারণে, সুখশ্রাব্য ও কৌতূহলোদ্দীপক ছিল, যে গল্পগুলো বাসুদেব দাশগুপ্তকে তিনি শোনাতেন । অনেকে মনে করেন বাসুদেব দাশগুপ্তের গল্পগুলোর উৎস হলো অবনী ধরের অভিজ্ঞতা । লেখালিখি না করেও অবনী ধর তাঁর জীবনযাপনের কারণে নিজেকে হাংরি আন্দোলনকারী মনে করতেন । হাংরি আন্দোলনকারীদের সঙ্গে খালাসিটোলায় ঢুঁ মারতেন । বাসুদেব দাশগুপ্ত ও শৈলেশ্বর ঘোষের প্ররোচনায় সোনাগাছির যৌনকর্মী বেবি, মীরা এবং দীপ্তির সঙ্গে নৈকট্য গড়ে ফেলেছিলেন ।
হাংরি আন্দোলনের সময়ে, উৎসাহদানকারী সম্পাদক ও স্তাবকদলের অভাবে, এবং অবনী ধরের সাহিত্যিক উচ্চাকাঙ্খার অনুপস্হিতিতে, তাঁর বলা কাহিনিগুলো লিখিত পাঠবস্তুর আকার নিতে পারেনি । জরুরি অবস্হার শেষে সারা পশ্চিমবাংলা জুড়ে লিটল ম্যাগাজিন বিস্ফোরণ ঘটলেও, সম্পাদকরা অবনীর গদ্য সম্পর্কে আগ্রহী হননি, মূলত তাঁর কথনভঙ্গীর ও রচনাকাঠামো বিদ্যায়তনিক সংরূপ বহির্ভূত ছিল বলে । একজন খালাসির গদ্যসন্দর্ভে যে যাযাবরতার নিবাস, যার উপকরণগুলো যাত্রাপথের খুদে অনির্ণেয়তায় তাৎপর্যময়, যার বিন্যাসে ভাসমান পরিভ্রমণের অনুন্মোচিত বাচন, স্নায়ুভাষায় রচিত সেরকম স্বতঃজাত কৃৎপ্রকরণ, স্বীকৃতি পায়নি লিটল ম্যাগাজিন স্তরেও । যেহেতু অবনীর পাঠবস্তু আত্মমগ্নতাকে অতিক্রম করে যায়, এবং তাঁর বাকব্যঞ্জনা বদ্ধসমাপ্তির কাঠামোটাকেই উপহাস করে, প্রধাগত আলোচকদের দৃষ্টিও তিনি আকর্ষণ করতে পারেননি ।
অবনীর ও তাঁর আত্মীয় পরিজনের পরিবারে নিরুদ্দিষ্ট, সাধু, সন্ন্যাসী, মোহন্ত, ভিখারি-বৈষ্ণব, বাউল ইত্যাদির পূর্বেতিহাস থাকার কারণে অবনীর ভবিষ্যৎ নিয়ে তাঁর মা চিন্তিত ছিলেন । বয়ঃসন্ধি অতিক্রান্ত সন্ধিক্ষণে তাঁর ছেলে হয়তো কোনও বন্দরশহর থেকে বিদেশিনী বিয়ে করে বা না-করে সঙ্গে এনে একদিন হাজির হবেন, এমন দুশ্চিন্তাও লাবণ্য ধরের ছিল । ছেলের চরিত্রে অভিজ্ঞতাজনিত পার্থক্যও তিনি লক্ষ্য করে থাকবেন । তিনি অবনীকে বললেন জাহাজের চাকরি ছেড়ে বাড়ি ফিরে আসতে । খালাসির চাকরি ছেড়ে ১৯৫৫ সালে ফিরে এলেন অবনী । বুড়োমা মারা যেতে তাঁর মা মধুপুরে একা হয়ে পড়েছিলেন । অবনী দেশে ফিরে চেতলার একটা বস্তিঘরে, মামার বাড়ির কাছে, বাসা ভাড়া নিয়ে মাকে মধুপুর থেকে নিয়ে এলেন । ১৯৫৫ থেকে ১৯৬৩, এই আট বছর টাকা রোজগারের জন্য নানা রকম জীবিকার অভিজ্ঞতা হলো অবনীর — ক্রেন-ড্রেজার-ডাম্পার অপারেটার, লরি-ট্যাকসি-প্রায়ভেট মোটরগাড়ি চালক, রেলওয়ে ক্যাটারিঙের বেয়ারা, কোককয়লা ফেরি, ঠোঙা ও প্যাকেট তৈরি, পোস্টার-ফেস্টুন লেখা ইত্যাদি, অসংগঠিত শ্রমিকের জন্য যে-ধরণের কাজ পাওয়া যায় সবই করলেন । ১৯৬২ সালে অবনীর মা পাত্রী নির্বাচন করে সাধনার সঙ্গে তাঁর বি্য়ে দেন ।
অবনী তাঁর সংসার ইতিমধ্যে চেতলা থেকে নতুন গড়ে-ওঠা উদ্বাস্তু পুনর্বাসন কলোনি অশোকনগরে তুলে নিয়ে যান । তখন সেখানে স্হানীয় স্বায়ত্বশাসনের পরিকাঠামো বিশেষ ছিল না । তিনি নবতর অভিজ্ঞতার সামনে পড়লেন অশোকনগরে । তিনি এও দেখলেন যে, যাঁদের মাঝে তিনি বসবাস করতে এলেন, তাঁরা পপতিদিনকার মূর্ত নাগরিক অসুবিধা ও জাগতিক দুঃখকষ্টে ও অভাব প্রতিকারের বদলে সোভিয়েত রাষ্ট্র, চিন, ভিয়েৎনাম, কিউবা, আমেরিকা, দিল্লী ইত্যাদি সুদূরবর্তী বিমূর্ত অদরকারি তর্কাতর্কিতে সময় ও ক্ষমতা অপচয় অপচয় করে আনন্দ পান । অর্থাৎ সুপ্রাইণ্ডিভিজুয়াল বা অধিব্যক্তিক ম্যাক্রোলেভেল ভাবুকদের পশ্চিমবাংলার মাটিপৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্কহীন তৎপরতার প্রেক্ষিতে, তাঁর মাইক্রোলেভেল খালাসিত্ব তাঁকে কল্যাণকামীতার স্বাভাবিক সনাতন মূল্যবোধে হায়ারার্কিবর্জিত করে রেখেছিল, এবং সেই ভূমিজ প্রবৃত্তিকে অবনী ধর কাজে লাগালেন ।
তিনি এবং আরও কয়েকজন মিলে, বিশেষ করে শিক্ষক সমর ঘোষ, অশোকনগরে ডাকঘর বসানো, পৌরসভা গঠন, অসামাজিক কাজকারবার বন্ধ ইত্যাদির উদ্যোগ নিলেন । উদ্যোগটিকে কন্ঠস্বর দেবার জন্য, এবং তাঁদের অভাব-অভিযোগ যাতে কর্তাব্যক্তিদের কানে পৌঁছোয়, ১৯৬৪ সালে পপকাশ করা আরম্ভ করলেন ‘অশোকনগর বার্তা’ নামে একটি পাক্ষিক সংবাদপত্র, যেটি ছিল ওই অঞ্চলের প্রথম পঞ্জিকৃত সংবাদপত্র । পত্রিকাটির আয়ু ছিল তিন বছর, সম্ভবত যথেষ্ট । পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত থাকলেও, নিজের অভিজ্ঞতাকে কথাবস্তুতে রূপান্তরিত করে ছাপাবার কথা তাঁর মনে আসেনি কখনও ; পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত অন্যেরাও তাঁর মুখে ঘটনা শুনেও তাঁকে লিখতে বলেননি । সম্ভবত সমাজচিন্তনকে আত্মসাৎ করে ব্যক্তি-ক্রিয়াকরণের চিন্তা-পরিসর লালিত হবার মতো পৃথকত্ববোধ জাগার সুযোগ বা মনস্হিতি তাঁর হয়নি । ১৯৬৩ সাল থেকে চাকুরিহীন অবনীর কাছে আপনা থেকেই পরিত্যক্ত হয়েছিল ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার দর্শন ।
অবনী ধরের কথাবস্তুগুলোকে দুটি পর্বে চি্হ্ণিত করা যায় । প্রথম পর্বটি ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় পর্বটি ২০০০ সালের পর । মাঝে লেখা ছেড়ে দিয়েছিলেন । প্রথম পর্বে তিনি ছিলেন অর্থস্রোতহীন এবং কোনও সাহিত্যিক স্বকীয়তা আনার প্রয়াস করেননি । তা আপনা থেকে হয়ে গিয়েছিল তাঁর অনির্মিত লেখক-প্রতিস্বের কারণে । অবনী ধরের ডিসকোর্স, কখনও খালাসির, কখনও বা অসংগঠিত শ্রমিক বা কর্মহীনের, ভূপ্রকৃতির উথ্থানভূমিলব্ধ, স্হানিক, অবিমিশ্র, মুক্ত, যৌগিক, বর্ণিল, অনুভূমিক, প্রতিসংস্হাপিত, কৌমনিষ্ঠ এবং অতিজ্ঞাপনমূলক । প্রথম লেখাটি, ‘আমার দুঃখী মা’ রচনার পর তিনি তা লাবণ্য ধরকেই পড়ে শুনিয়েছিলেন । স্তম্ভিত মা কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর. বলেছিলেন, ‘সত্য কথাই ল্যাখছস।’
দ্বিতীয় পর্বের শুরু ২০০০ সালে । এই পর্বে অবনীর গদ্য-কাঠামোয় কয়েকটি কারণে সাইত্যিকতা এসে গেছে । তাঁর স্ত্রী, আরও কয়েকজন সহকর্মীর সঙ্গে একজোট হয়ে মামলা করে ১৯৯০ সালে চাকরি পাবার পর অবনীর আর্থিক অনিশ্চয়তা কাটে । তাঁর মেয়ে ইতিহাসে স্নাতকোত্তর ও বি এড এবং ছেলে বি এ পাশ করেন । অর্থাৎ প্রথম পর্বের জ্ঞান পরিমণ্ডলটি, তাঁর মেয়ে ও ছেলের প্রভাবে ক্রমশ অপসারিত হয়ে বাড়ির মধ্যে একটি ভিন্ন, যা অবনীর কাছে তুলনামূলকভাবে উচ্চতর ঠেকে থাকবে, জ্ঞানপরিমণ্ডলের প্রবেশ ঘটিয়েছে । তৃতীয়ত, তাঁর প্রথম পর্বের রচনাগুলো, অন্তত কিছু সাহিত্যপাঠকের, হাতে গোনা হলেও, দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকবে, যাঁদের পাঠ-প্রতিক্রিয়ায় তিনি উৎসাহিত হয়ে থাকবেন গদ্যগুলোকে একটি সাহিত্যিক আদল-আদরা দেবার । দ্বিতীয় পর্বের কথাবস্তুগুলোর গদ্যবিন্যাসে ধরা পড়ে যে প্রথাবাহিত গদ্যসাহিত্যের সঙ্গে, যেগুলো তাঁর ছেলে-মেয়ে নিজেরা পড়ার জন্য বাড়িতে এনে থাকবেন, তাঁর যোগাযোগ ঘটেছে । অবনী নিজে চেষ্টা করলেও, এই বয়সে পৌঁছে, তাঁর পক্ষে মুকুরবিম্ব গড়া সম্ভবপর হয়নি, এবং তাঁর অপরত্ববোধ ও সাহিত্যিক অপরত্ব মুছে যায়নি । প্রথম ও দ্বিতীয়, দুটি পর্বেই, তাঁর জীবনজিজ্ঞাসা তাড়িত হয়েছে অপরত্ববোধের অবস্হাননজনিত বিপর্যয় দ্বারা। আর কোনো বাঙালি সাহিত্যিকের কথাবস্তুতে, অপরত্ববোধের মাত্রাগুলোকে, অবনীর মতো করে ইতোপূর্বে উপস্হাপন করতে দেখা যায়নি । তাঁর মস্তিষ্কে আতিথ্য নেয়া কথাকারটি নিজেরই স্মৃতির ঐতিহাসিক হিসেবে অবনীর সামনে উদয় হয়েছে কখনও-সখনও, যিনি অতীতকে বাঁচিয়ে তুলতে চেষ্টা করছেন না বা অতীতে বেঁচে থাকার কথা বলছেন না ; আসলে কথাকার ওই দূরবর্তী এবং নিকট অতীতের লোপাট হয়ে যাওয়া ও তাকে বাগে আনার বাচনক্রীড়ায় অংশগ্রহণকারীরূপে ‘অপর প্রতিসন্দর্ভের’ সতর্কতাগুলো জাহির করছেন ।
দুই
উত্তরবঙ্গে হাংরি জেনারেশনের প্রসার সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে, হাংরি পত্রিকা ‘কনসেনট্রেশন ক্যাম্প’ এর সম্পাদক অলোক গোস্বামী এই কথাগুলো লিখেছিলেন, তা থেকে অবনিবনার যৎসামান্য আইডিয়া হবে, কিন্তু এই অবনিবনার সঙ্গে পরাবাস্তববাদীদের নিজেদের অবনিবনারে যথেষ্ট মিল আছে :-
“নব্বুই দশকে সদ্য প্রকাশিত কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প বগলে নিয়ে এক ঠা ঠা দুপুরে আমি হাজির হয়েছিলাম শৈলেশ্বরের বাড়ির গেটে। একা। ইচ্ছে ছিল শৈলেশ্বরের সঙ্গে মুখোমুখি বসে যাবতীয় ভুল বোঝাবুঝি নিয়ে খোলাখুলি কথা বলবো। যেহেতু স্মরণে ছিল শৈলেশ্বরের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের স্মৃতি তাই আস্থা ছিল শৈলেশ্বরের প্রজ্ঞা,ব্যক্তিত্ব,যুক্তিবোধ তথা ভদ্রতাবোধের ওপর। দৃঢ় বিশ্বাস ছিল শৈলেশ্বর আমাদের ভুলগুলো ধরিয়ে দেবেন এবং যৌথ আলোচনাই পারবে সব ভুল বোঝাবুঝি মিটিয়ে নতুন উদ্যমে একসাথে পথ চলা শুরু করতে। কিন্তু দুভার্গ্য বশতঃ তেমন কিছু ঘটলো না। বেল বাজাতেই গেটের ওপারে শৈলেশ্বর। আমাকে দেখেই ভ্রূ কুঁচকে ফেললেন।
--কী চাই!
মিনমিন করে বললাম, আপনার সঙ্গে কথা বলবো।
--কে আপনি?
এক এবং দুই নম্বর প্রশ্নের ভুল অবস্থান দেখে হাসি পাওয়া সত্বেও চেপে গিয়ে নাম বললাম।
--কি কথা?
--গেটটা না খুললে কথা বলি কিভাবে!
--কোনো কথার প্রয়োজন নেই। চলে যান।
--এভাবে কথা বলছেন কেন?
--যা বলছি ঠিক বলছি। যান। নাহলে কিন্তু প্রতিবেশীদের ডাকতে বাধ্য হবো।
এরপর স্বাভাবিক কারণেই খানিকটা ভয় পেয়েছিলাম কারণ আমার চেহারাটা যেরকম তাতে শৈলেশ্বর যদি একবার ডাকাত, ডাকাত বলে চেঁচিয়ে ওঠেন তাহলে হয়ত জান নিয়ে ফেরার সুযোগ পাবো না। তবে 'ছেলেধরা' বলে চেল্লালে ভয় পেতাম না। সমকামিতার দোষ না থাকায় নির্ঘাত রুখে দাঁড়াতাম।
ভয় পাচ্ছি অথচ চলেও যেতে পারছি না। সিদ্ধান্তে পৌঁছতে গেলে আরও খানিকটা জানা বোঝা জরুরি।
--ঠিক আছে, চলে যাচ্ছি। তবে পত্রিকার নতুন সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে সেটা রাখুন।
এগিয়ে আসতে গিয়েও থমকে দাঁড়ালেন শৈলেশ্বর।
--কোন পত্রিকা?
--কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প।
--নেব না। যান।
এরপর আর দাঁড়াইনি। দাঁড়ানোর প্রয়োজনও ছিল না। ততক্ষণে বুঝে ফেলেছি ব্যক্তি শৈলেশ্বর ঘোষকে চিনতে ভুল হয়নি আমাদের। আর এই সমঝদারি এতটাই তৃপ্তি দিয়েছিল যে অপমানবোধ স্পর্শ করারই সুযোগ পায়নি।”
শৈলেশ্বর ঘোষের হয়তো মনে হয়েছিল যে কলকাতায় তিনি হাংরি আন্দোলনের যে কেন্দ্র গড়ে তুলতে চাইছেন তাতে ফাটল ধরাবার চেষ্টা করা হচ্ছে । তাঁর আচরণ ছিল হুবহু আঁদ্রে ব্রেতঁর মতন । পরাবাস্তববাদ আন্দোলনে আঁদ্রে ব্রেতঁর সঙ্গে অনেকের সম্পর্ক ভালো ছিল না, দল বহুবার ভাগাভাগি হয়েছিল, অথচ সেসব নিয়ে বাঙালি আলোচকরা তেমন উৎসাহিত নন, যতোটা হাংরি আন্দোলনের দল-ভাগাভাগি নিয়ে । ইংরেজিতে মৈত্রেয়ী ভট্টাচার্য চৌধুরী হাংরি আন্দোলন নিয়ে ‘দি হাংরিয়ালিস্টস’ নামে একটি বই লিখেছেন, পেঙ্গুইন র্যাণ্ডাম হাউস থেকে প্রকাশিত । সেই বইটি বাংলা পত্রপত্রিকায় আলোচিত হল না ।
আনন্দবাজার পত্রিকায় ১৬ জুন ২০১৩ তারিখে গৌতম চক্রবর্তী হাংরি আন্দোলন সম্পর্কে এই কথাগুলো লিখেছিলেন ; তাতেও রয়েছে টিটকিরি যা তিনি পরাবাস্তববাদীদের সম্পর্কে কখনও বলেছেন কিনা জানি না । উনি লিখেছিলেন :
“মানুষ, ঈশ্বর, গণতন্ত্র ও বিজ্ঞান পরাজিত হয়ে গেছে। কবিতা এখন একমাত্র আশ্রয়।... এখন কবিতা রচিত হয় অর্গ্যাজমের মতো স্বতঃস্ফূর্তিতে।
১৯৬২ সালে এই ভাষাতেই কলেজ স্ট্রিট কফি হাউস থেকে খালাসিটোলা, বারদুয়ারি অবধি সর্বত্র গোপন বিপ্লবী আন্দোলনের ব্লু প্রিন্টের মতো ছড়িয়ে পড়ে একটি ম্যানিফেস্টো। ২৬৯ নেতাজি সুভাষ রোড, হাওড়া থেকে প্রকাশিত এই ম্যানিফেস্টোর ওপরে লেখা হাংরি জেনারেশন। নীচের লাইনে তিনটি নাম। স্রষ্টা: মলয় রায়চৌধুরী। নেতৃত্ব: শক্তি চট্টোপাধ্যায়। সম্পাদনা: দেবী রায়।
তখনও কলেজ স্ট্রিটের বাতাসে আসেনি বারুদের গন্ধ, দেওয়ালে লেখা হয়নি ‘সত্তরের দশক মুক্তির দশক’। কিন্তু পঞ্চাশ পেরিয়ে-যাওয়া এই ম্যানিফেস্টোর গুরুত্ব অন্যত্র। এর আগে ‘ভারতী’, ‘কবিতা’, ‘কৃত্তিবাস’, ‘শতভিষা’ অনেক কবিতার কাগজ ছিল, সেগুলি ঘিরে কবিরা সংঘবদ্ধও হতেন। কিন্তু এই ভাবে সাইক্লোস্টাইল-করা ম্যানিফেস্টো আগে কখনও ছড়ায়নি বাংলা কবিতা।
ওটি হাংরি আন্দোলনের দ্বিতীয় ম্যানিফেস্টো। প্রথম ম্যানিফেস্টোটি বেরিয়েছিল তার কয়েক মাস আগে, ১৯৬১ সালের নভেম্বর মাসে। ইংরেজিতে লেখা সেই ম্যানিফেস্টো জানায়, কবিতা সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যায় না, বিভ্রমের বাগানে পুনরায় বৃক্ষরোপণ করে না। ‘Poetry is no more a civilizing manoeuvre, a replanting of bamboozled gardens.’ বিশ্বায়নের ঢের আগে ইংরেজি ভাষাতেই প্রথম ম্যানিফেস্টো লিখেছিলেন হাংরি কবিরা। কারণ, পটনার বাসিন্দা মলয় রায়চৌধুরী ম্যানিফেস্টোটি লিখেছিলেন। পটনায় বাংলা ছাপাখানা ছিল না, ফলে ইংরেজি।
দুটি ম্যানিফেস্টোতেই শেষ হল না ইতিহাস। হাংরি আসলে সেই আন্দোলন, যার কোনও কেন্দ্র নেই। ফলে শহরে, মফস্সলে যে কোনও কবিই বের করতে পারেন তাঁর বুলেটিন। ১৯৬৮ সালে শৈলেশ্বর ঘোষ তাঁর ‘মুক্ত কবিতার ইসতাহার’-এ ছাপিয়ে দিলেন ‘সমস্ত ভন্ডামির চেহারা মেলে ধরা’, ‘শিল্প নামক তথাকথিত ভূষিমালে বিশ্বাস না করা’, ‘প্রতিষ্ঠানকে ঘৃণা করা’, ‘সভ্যতার নোনা পলেস্তারা মুখ থেকে তুলে ফেলা’ ইত্যাদি ২৮টি প্রতিজ্ঞা। পরে বন্ধুদের মধ্যে ঝগড়া বাধবে। মলয় ব্যাংকের চাকরি নিয়ে বাইরে চলে যাবেন। শৈলেশ্বর, সুবো আচার্য এবং প্রদীপ চৌধুরীরা বলবেন, ‘মলয় বুর্জোয়া সুখ ও সিকিয়োরিটির লোভে আন্দোলন ছেড়ে চলে গিয়েছে।’কী রকম লিখতেন হাংরিরা? বছর দুয়েক আগে সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের ‘বাইশে শ্রাবণ’ ছবিতে গৌতম ঘোষের চরিত্রটি লেখা হয়েছিল হাংরি কবিদের আদলে।
‘জেগে ওঠে পুরুষাঙ্গ নেশার জন্য হাড় মাস রক্ত ঘিলু শুরু করে কান্নাকাটি
মনের বৃন্দাবনে পাড়াতুতো দিদি বোন বউদিদের সঙ্গে শুরু হয় পরকীয়া প্রেম’,
লিখেছিলেন অকালপ্রয়াত ফালগুনী রায়। র্যাঁবো, উইলিয়াম বারোজ এবং হেনরি মিলারের উদাহরণ বারে বারেই টেনেছেন হাংরিরা। ঘটনা, এঁরা যত না ভাল কবিতা লিখেছেন, তার চেয়েও বেশি ঝগড়া করেছেন। এবং তার চেয়েও বেশি বার গাঁজা, এলএসডি, মেস্কালিন আর অ্যাম্ফিটোমাইন ট্রিপে গিয়েছেন।
অতএব, সাররিয়ালিজ্ম বা অন্য শিল্প আন্দোলনের মতো বাঙালি কবিদের ম্যানিফেস্টোটি কোনও দিন গুরুত্বপূর্ণ হয়নি। কিন্তু ‘হাংরি’রা আজও মিথ। এক সময় ‘মুখোশ খুলে ফেলুন’ বলে তৎকালীন মন্ত্রী, আমলা, সম্পাদকদের বাড়িতে ডাকযোগে তাঁরা মুখোশ পাঠিয়ে দিয়েছেন। আবার এক সময় ‘প্রচন্ড বৈদ্যুতিক ছুতার’ কবিতাটি লেখার জন্য অশ্লীলতার মামলা হল মলয় রায়চৌধুরীর বিরুদ্ধে। উৎপলকুমার বসু, সুবিমল বসাকের বিরুদ্ধে জারি হল গ্রেফতারি পরোয়ানা।
রাষ্ট্র ও আদালত কী ভাবে কবিতাকে দেখে, সেই প্রতর্কে ঢুকতে হলে ১৯৬৫ সালে মলয় রায়চৌধুরীর বিরুদ্ধে মামলাটি সম্পর্কে জানা জরুরি। শক্তি চট্টোপাধ্যায় কাঠগড়ায় উঠেছেন মলয়ের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে। পাবলিক প্রসিকিউটরের জিজ্ঞাসা, ‘প্রচন্ড বৈদ্যুতিক ছুতার’ কবিতাটা পড়ে আপনার কী মনে হয়েছে?
শক্তি: ভাল লাগেনি।
প্রসিকিউটর: অবসিন কি? ভাল লাগেনি বলতে আপনি কী বোঝাতে চাইছেন?
শক্তি: ভাল লাগেনি মানে জাস্ট ভাল লাগেনি। কোনও কবিতা পড়তে ভাল লাগে, আবার কোনওটা ভাল লাগে না।
শক্তি সাক্ষ্য দিয়েছিলেন মলয়ের বিরুদ্ধে। কয়েক মাস পরে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় মলয়ের সমর্থনে...
প্রসিকিউটর: কবিতাটা কি অশ্লীল মনে হচ্ছে?
সুনীল: কই, না তো। আমার তো বেশ ভাল লাগছে। বেশ ভাল লিখেছে।
প্রসিকিউটর: আপনার শরীরে বা মনে খারাপ কিছু ঘটছে?
সুনীল: না, তা কেন হবে? কবিতা পড়লে সে সব কিছু হয় না।
একই মামলায় শক্তি ও সুনীল পরস্পরের বিরুদ্ধে। তার চেয়েও বড় কথা, ’৬৫ সালে এই সাক্ষ্য দেওয়ার আগের বছরই সুনীল আইওয়া থেকে মলয়কে বেশ কড়া একটি চিঠি দিয়েছিলেন, ‘লেখার বদলে আন্দোলন ও হাঙ্গামা করার দিকেই তোমার ঝোঁক বেশি। রাত্রে তোমার ঘুম হয় তো? মনে হয়, খুব একটা শর্টকাট খ্যাতি পাবার লোভ তোমার।’ ব্যক্তিগত চিঠিতে অনুজপ্রতিম মলয়কে ধমকাচ্ছেন, কিন্তু আদালতে তাঁর পাশে গিয়েই দাঁড়াচ্ছেন। সম্ভবত, বন্ধু-শত্রু নির্বিশেষে অনুজ কবিদের কাছে সুনীলের ‘সুনীলদা’ হয়ে ওঠা হাংরি মামলা থেকেই। প্রবাদপ্রতিম কৃত্তিবাসী বন্ধুত্বের নীচে যে কত চোরাবালি ছিল, তা বোঝা যায় উৎপলকুমার বসুকে লেখা সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের একটি চিঠি থেকে, ‘প্রিয় উৎপল, একদিন আসুন।...আপনি তো আর শক্তির মতো ধান্দায় ঘোরেন না।’
তা হলে কি হাংরি আন্দোলন বাংলা সাহিত্যে প্রভাবহীন, শুধুই কেচ্ছাদার জমজমাট এক পাদটীকা? দুটি কথা। হাংরিদের প্রভাবেই কবিতা-সংক্রান্ত লিট্ল ম্যাগগুলির ‘কৃত্তিবাস’, ‘শতভিষা’ গোছের নাম বদলে যায়। আসে ‘ক্ষুধার্ত’, ‘জেব্রা’, ‘ফুঃ’-এর মতো কাগজ। সেখানে কবিতায় বাঁকাচোরা ইটালিক্স, মোটাদাগের বোল্ড ইত্যাদি হরেক রকমের টাইপোগ্রাফি ব্যবহৃত হত। পরবর্তী কালে সুবিমল মিশ্রের মতো অনেকেই নিজেকে হাংরি বলবেন না, বলবেন ‘শুধুই ছোট কাগজের লেখক’। কিন্তু তাঁদের গল্প, উপন্যাসেও আসবে সেই টাইপোগ্রাফিক বিভিন্নতা। তৈরি হবে শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন। হাংরিরা না এলে কি নব্বইয়ের দশকেও হানা দিতেন পুরন্দর ভাট?
আসলে, ম্যানিফেস্টোর মধ্যেই ছিল মৃত্যুঘণ্টা। ’৬২ সালে হাংরিদের প্রথম বাংলা ম্যানিফেস্টোর শেষ লাইন, ‘কবিতা সতীর মতো চরিত্রহীনা, প্রিয়তমার মতো যোনিহীনা ও ঈশ্বরীর মতো অনুষ্মেষিণী।’ হাংরিরা নিজেদের যত না সাহিত্যবিপ্লবী মনে করেছেন, তার চেয়েও বেশি যৌনবিপ্লবী।”
তিন
১৯১৭ সালে গিয়ম অ্যাপলিনেয়ার “সুররিয়ালিজম” অভিধাটি তৈরি করেছিলেন, যার অর্থ ছিল বাস্তবের অতীত। শব্দটি প্রায় লুফে নেন আঁদ্রে ব্রেতঁ, নতুন একটি আন্দোলন আরম্ভ করার পরিকল্পনা নিয়ে, যে আন্দোলনটি হবে পূর্ববর্তী ডাডাবাদী আন্দোলন থেকে ভিন্ন । ত্রিস্তঁ জারা উদ্ভাবিত ডাডা আন্দোলন থেকে সরে আসার কারণ হল ব্রেতঁ সহ্য করতে পারতেন না ত্রিস্তঁ জারাকে, কেননা কবি-শিল্পী মহলে প্রতিশীল্পের জনক হিসাবে ত্রিস্তঁ জারা খ্যাতি পাচ্ছিলেন। আঁদ্রে ব্রেতঁ সুররিয়ালিজম তত্বটির একমাত্র ব্যাখ্যাকারী হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে আরম্ভ করেন। ১৯১৯ সালে ত্রিস্তঁ জারাকে কিন্তু ব্রেতঁ চিঠি লিখে প্যারিসে আসতে বলেছিলেন । একইভাবে ‘হাংরি’ শব্দটি মলয় রায়চৌধুরী পেয়েছিলেন কবি জিওফ্রে চসার থেকে । এই ‘হাংরি’ শব্দটি নেয়ার জন্য মলয় রায়চৌধুরীকে যেভাবে আক্রমণ করা হয়েছে, তেমন কিছুই করা হয়নি আঁদ্রে ব্রেতঁ ও ত্রিস্তঁ জারা সম্পর্কে । মলয় রায়চৌধুরী হাংরি জেনারেশন আন্দোলন ঘোষণা করেন ১৯৬৫ সালের পয়লা নভেম্বর একটি লিফলেট প্রকাশের মাধ্যমে ।
পরাবাস্তববাদী আন্দোলনে, প্রথম থেকেই, আঁদ্রে ব্রেতঁ’র সঙ্গে অনেক পরাবাস্তববাদীর সদ্ভাব ছিল না, কিন্তু পরাবাস্তববাদ বিশ্লেষণের সময়ে আলোচকরা তাকে বিশেষ গুরুত্ব দেন না । আমরা যদি বাঙালি আলোচকদের কথা চিন্তা করি, তাহলে দেখব যে তাঁরা হাংরি জেনারেশন বা ক্ষুধার্ত আন্দোলন বিশ্লেষণ করার সময়ে হাংরি জেনারেশনের সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে অত্যধিক চিন্তিত, হাংরি আন্দোলনকারীদের সাহিত্য অবদান নিয়ে নয় । ব্যাপারটা বিস্ময়কর নয় । তার কারণ অধিকাংশ আলোচক হাংরি জেনারেশনের সদস্যদের বইপত্র সহজে সংগ্রহ করতে পারেন না এবং দ্বিতীয়ত সাংবাদিক-আলোচকদের কুৎসাবিলাসী প্রবণতা ।
আঁদ্রে ব্রেতঁ তাঁর বন্ধু পল এলুয়ার, বেনিয়ামিন পেরে, মান রে, জাক বারোঁ, রেনে ক্রেভালl, রোবের দেসনস, গিয়র্গে লিমবোর, রোজের ভিত্রাক, জোসেফ দেলতিল, লুই আরাগঁ ও ফিলিপে সুপোকে নিয়ে ১৯১৯ পরাবাস্তববাদ আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন । কিছুকাল পরে, রাজনৈতিক ভাবাদর্শের কারণে তাঁর সঙ্গে লুই আরাগঁর ঝগড়া বেধে গিয়েছিল । মার্সেল দ্যুশঁ, ত্রিস্তঁ জারা এবং আঁদ্রে ব্রেতঁ, উভয়ের সঙ্গেই ছিলেন, এবং দুটি দলই তাঁকে গুরুত্ব দিতেন, দ্যুশঁ’র অবাস্তব ও অচিন্ত্যনীয় ভাবনার দরুন।
পরাবাস্তব আন্দোলনের আগে জুরিখে ডাডাবাদী আন্দোলন আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল এবং আঁদ্রে ব্রেতঁ পরাবাস্তববাদের অনুপ্রেরণা পান ডাডা আন্দোলনের পুরোধা ত্রিস্তঁ জারার কাছ থেকে, কিন্তু ব্রেতঁ চিরকাল তা অস্বীকার করে্ছেন । ডাডা ছিল শিল্পবিরোধী আভাঁ গার্দ আন্দোলন ; অবশ্য প্রতিশিল্পও তো শিল্প । ডাডাবাদের রমরমার কারণে ত্রিস্তঁ জারার সঙ্গে ব্রেতঁর সম্পর্ক দূষিত হয়ে যায় ; একজন অন্যজনের নেতৃত্ব স্বীকার করতে চাইতেন না । ডাডা (/ˈdɑːdɑː/) বা ডাডাবাদ (দাদাবাদ নামেও পরিচিত) ছিল ২০ শতকের ইউরোপীয় ভিন্নচিন্তকদের একটি সাহিত্য-শিল্প আন্দোলন, যার প্রাথমিক কেন্দ্র ছিল সুইজারল্যান্ডের জুরিখে ক্যাবারে ভলতেয়ার ( ১৯১৬ নাগাদ ) এবং নিউ ইয়র্কে (প্রায় ১৯১৫ নাগাদ)। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় ডাডা আন্দোলন গড়ে ওঠে সেইসব শিল্পীদের নিয়ে, যাঁরা পুঁজিবাদী সমাজের যুক্তি, কারণ বা সৌন্দর্যের ধারণা মানতেন না, বরং তাঁদের কাজের মাধ্যমে প্রকাশ করতেন আপাত-অর্থহীন, উদ্ভট, অযৌক্তিক এবং বুর্জোয়া-বিরোধী প্রতিবাদী বক্তব্য । আন্দোলনটির শিল্পচর্চা প্রসারিত হয়েছিল দৃশ্যমান, সাহিত্য ও শব্দ মাধ্যমে, যেমন- কোলাজ, শব্দসঙ্গীত, কাট-আপ লেখা, এবং ভাস্কর্য। ডাডাবাদী শিল্পীরা হানাহানি, যুদ্ধ এবং জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে অসন্তোষ প্রকাশ করতেন এবং গোঁড়া বামপন্থীদের সাথে তাঁদের রাজনৈতিক যোগাযোগ ছিল।
যুদ্ধ-পূর্ববর্তী প্রগতিবাদীদের মধ্যেই ডাডার শিকড় লুকিয়ে ছিল। শিল্পের সংজ্ঞায় পড়েনা এমন সব সৃষ্টিকর্মকে চিহ্নিত করার জন্য ১৯১৩ সালে "প্রতি-শিল্প" শব্দটি চালু করেছিলেন মার্সেল দ্যুশঁ । কিউবিজম এবং কোলাজ ও বিমূর্ত শিল্পের অগ্রগতিই হয়তো ডাডা আন্দোলনকে বাস্তবতার গন্ডী থেকে বিচ্যুত হতে উদ্বুদ্ধ করে। আর শব্দ ও অর্থের প্রথানুগত সম্পর্ক প্রত্যাখ্যান করতে ডাডাকে প্রভাবিত করে ইতালীয় ভবিষ্যতবাদী এবং জার্মান এক্সপ্রেশনিস্টগণ । আলফ্রেড জ্যারির উবু রোই (১৮৯৬) এবং এরিক স্যাটির প্যারেড (১৯১৬-১৭) প্রভৃতি লেখাগুলোকে ডাডাবাদী রচনার আদিরূপ বলা যেতে পারে। ডাডা আন্দোলনের মূলনীতিগুলো প্রথম সংকলিত হয় ১৯১৬ সালে হুগো বলের ডাডা ম্যানিফেস্টোতে। এই ম্যানিফেস্টোর প্রভাবে পরবর্তিকালে ব্রেতঁ সুররিয়ালিস্ট ম্যানিফেস্টো লিখতে অনুপপ্রাণিত হন -- এই কথা শুনতে ব্রেতঁ’র ভালো লাগত না এবং সেকারণে তিনি বহু সঙ্গীকে এক-এক করে আন্দোলন থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন । তাছাড়া ব্রেতঁ মনে করতেন ডাডাবাদীরা নৈরাজ্যবাদী বা অ্যানার্কিস্ট, যখন কিনা তিনি একজন কমিউনিস্ট ।
ডাডা আন্দোলনে ছিল জনসমাবেশ, মিছিল ও সাহিত্য সাময়িকীর প্রকাশনা; বিভিন্ন মাধ্যমে শিল্প, রাজনীতি এবং সংস্কৃতি নিয়ে তুমুল আলোচনা হতো। আন্দোলনের প্রধান ব্যক্তিত্বরা ছিলেন হুগো বল, মার্সেল দ্যুশঁ, এমি হেনিংস, হানস আর্প, রাউল হাউসম্যান, হানা হৌক, জোহান বাডার, ত্রিস্তঁ জারা, ফ্রান্সিস পিকাবিয়া, রিচার্ড হিউলসেনব্যাক, জর্জ গ্রোস, জন হার্টফিল্ড, ম্যান রে, বিয়াট্রিস উড, কার্ট শ্যুইটার্স, হানস রিখটার এবং ম্যাক্স আর্নেস্ট। অন্যান্য আন্দোলন, শহরতলীর গান এসবের পাশাপাশি পরাবাস্তববাদ, নব্য বাস্তবতা, পপ শিল্প এবং ফ্লক্সেস প্রভৃতি গোষ্ঠীগুলোও ডাডা আন্দোলন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। এই আন্দোলনের অনেকে সুররিয়ালিস্ট আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন ।
পরাবাস্তববাদ আন্দোলনে যাঁরা ব্রেতঁর সঙ্গে একে-একে যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের অন্যতম হলেন ফিলিপে সুপো, লুই আরাগঁ, পল এলুয়ার, রেনে ক্রেভাল, মিশেল লেইরিস, বেনিয়ামিন পেরে, অন্তনাঁ আতো,জাক রিগো, রবের দেসনস, ম্যাক্স আর্নস্ত প্রমুখ । এঁদের অনেকে ডাডাবাদী আন্দোলন ত্যাগ করে পরাবাস্তববাদী আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯২৩ সালে যোগ দেন চিত্রকর আঁদ্রে মাসোঁ ও ইভস তাঙ্গুই । ১৯২১ সালে ভিয়েনায় গিয়ে ফ্রয়েডের সঙ্গে দেখা করেন ব্রেতঁ । ফ্রয়েডের ধারণাকে তিনি সাহিত্য ও ছবি আঁকায় নিয়ে আসতে চান । ফ্রয়েডের প্রভাবে ব্রেতঁ বললেন, সুররিয়ালিজমের মূলকথা হল অবচেতনমনের ক্রিয়াকলাপকে উদ্ভট ও আশ্চর্যকর সব রূপকল্প দ্বারা প্রকাশ করা। ডাডাবাদীরা যেখানে চেয়েছিলেন প্রচলিত সামাজিক মূল্যবোধকে নস্যাৎ করে মানুষকে এমন একটি নান্দনিক দৃষ্টির অধিকারী করতে যার মাধ্যমে সে ভেদ করতে পারবে ভণ্ডামি ও রীতিনীতির বেড়াজাল, পৌঁছাতে পারবে বস্তুর অন্তর্নিহিত সত্যে; সেখানে পরাবাস্তববাদ আরো একধাপ এগিয়ে বলল, প্রকৃত সত্য কেবলমাত্র অবচেতনেই বিরাজ করে। পরাবাস্তববাদী শিল্পীর লক্ষ্য হল তার কৌশলের মাধ্যমে সেই সত্যকে ব্যক্তি-অস্তিত্বের গভীর থেকে তুলে আনা।
সুররিয়ালিজমের প্রথম ইশতেহার প্রকাশ করেন ইয়ান গল। এ ইশতেহারটি ১৯২৪ সালের ১ অক্টোবর প্রকাশিত হয়। এর কিছুদিন পরেই ১৫ অক্টোবর আঁদ্রে ব্রেতঁ সুররিয়ালিজমের দ্বিতীয় ইশতেহারটি প্রকাশ করেন। তিনি ১৯৩০ সালে এ ধারার তৃতীয় ইশতেহারটিও প্রকাশ করেন। ইয়ান গল ও আঁদ্রে ব্রেতঁ—দুজনে দু দল সুররিয়ালিস্ট শিল্পীর নেতৃত্ব দিতেন। ইয়ান গলের নেতৃত্বে ছিলেন ফ্রান্সিস পিকাবিয়া, ত্রিস্তঁ জারা, মার্সেল আর্লেন্ড, জোসেফ ডেলটিল, পিয়েরে অ্যালবার্ট বিরোট প্রমুখ। আন্দ্রে ব্রেতঁর নেতৃত্বে ছিলেন লুই আরাগঁ, পল এলুয়ায়, রোবের ডেসনোস, জ্যাক বারোঁ, জর্জ ম্যালকিন প্রমুখ। এ দুটি দলেই ডাডাইজম আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ ছিলেন। অবশ্য ইয়ান গল ও আন্দ্রে ব্রেতঁ এই আন্দোলন নিয়ে প্রকাশ্য-রেশারেশিতে জড়িয়ে পড়েন। তখন থেকেই পরাবাস্তববাদীরা ছোটো-ছোটো গোষ্ঠীতে বিভাজিত হতে থাকেন, যদিও তাঁদের শিল্প ও সাহিত্যধারা ছিল একই । পরে আন্দোলনে যোগ দেন জোয়ান মিরো, রেমণ্ড কোয়েনু, ম্যাক্স মোরিজ, পিয়ের নাভিল, জাক আঁদ্রে বোইফার, গেয়র্গে মালকাইন প্রমুখ । জিয়োর্জিও দে চিরোকো এবং পাবলো পিকাসো অনেক সময়ে গোষ্ঠির কর্মকাণ্ডে অংশ নিতেন, তবে আন্দোলনের ঘোষিত সদস্য ছিলেন না।
সুররিয়ালিজম বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য ডাডাইজম থেকে নিলেও এই মতবাদটি, যে, ‘শিল্পের উৎস ও উপকরণ’ বিবেচনায় একটি অন্যটির চেয়ে স্বতন্ত্র্য। সুররিয়ালিজম আন্দোলনের সামনের সারিতে ছিলেন ফরাসি কবি আঁদ্রে ব্রেতঁ। তিনি শিল্প রচনায় ‘অচেতন মনের ওপর গুরুত্ব’ দেওয়ার জন্যে শিল্পীদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি মনে করতেন, ‘অচেতন মন হতে পারে কল্পনার অশেষ উৎস।’ তিনি অচেতন মনের ধারণাটি নিঃসন্দেহে সিগমুন্ড ফ্রয়েডের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। ডাডাবাদী শিল্পীরা শিল্পের উৎস ও উপকরণ আহরণে ‘অচেতন’ মনের ধারণা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না। সুররিয়ালিস্ট শিল্পীরা এসে অচেতন মনের উৎস থেকে শিল্প রচনার প্রতি গুরুত্ব দেন এবং সফলতাও লাভ করেন।
আঁদ্রে ব্রেতঁ মনে করতেন, ‘যা বিস্ময়কর, তা সবসময়ই সুন্দর’। অচেতন মনের গহীনেই বিস্ময়কর সুন্দরের বসবাস। তার সন্ধান করাই সাহিত্যিক-শিল্পীর যথার্থ কাজ। অচেতন মনের কারণেই সুররিয়ালিজমের কবি-শিল্পীরা গভীর আত্মঅনুসন্ধানে নামেন। মনের গহীন থেকে স্বপ্নময় দৃশ্যগুলো হাতড়ে বের করতে এবং মনের অন্তর্গত সত্য উন্মোচনে তাঁরা আগ্রহী ছিলেন। যার কারণে চেতন ও অচেতনের মধ্যে শিল্পীরা বন্ধন স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সুররিয়ালিস্ট শিল্পীরা অচেতন মনের সেই সব উপলব্ধিকে দৃশ্যে রূপ দিলেন যা পূর্বে কেউ কখনো করেনি। অচেতনের ভূমিতে দাঁড়িয়ে বাস্তব উপস্থাপনের কারণে খুব দ্রুতই এ মতবাদটি বিশ্ব শিল্পকলায় ‘অভিনবত্ব’ যোগ করতে সমর্থ হয়। এমনকী, পুঁজিবাদ-বিরোধী এই আন্দোলন থেকে উপকরণ সংগ্রহ করেছেন বহু বিখ্যাত বিজ্ঞাপন কোম্পানি ।
সুররিয়ালিজমকে ‘নির্দিষ্ট’ ছকে ফেলা কঠিন। সুররিয়ালিস্ট শিল্পীরা একই ছাতার নিচে বসবাস করে ছবি আঁকলেও এবং কবিতা লিখলেও, তাঁদের দৃষ্টি ও উপলব্ধির মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। ফলে এ মতবাদটি সম্পর্কে প্রত্যেকে ব্যাক্তিগত ভাবনা ভেবেছেন। ১৯২৯ সালে সালভাদর দালি এই আন্দোলনে যোগ দেন, যদিও তাঁর সঙ্গেও ব্রেতঁর বনিবনা হতো না । সালভাদর দালি মনে করতেন, ‘সুররিয়ালিজম একটি ধ্বংসাত্মক দর্শন এবং এটি কেবল তা-ই ধ্বংস করে যা দৃষ্টিকে সীমাবদ্ধ রাখে।’ অন্যদিকে জন লেলন বলেছেন, ‘সুররিয়ালিজম আমার কাছে বিশেষ প্রভাব নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। কেননা, আমি উপলব্ধি করেছিলাম আমার কল্পনা উন্মাদনা নয়। বরং সুররিয়ালিজমই আমার বাস্তবতা।’ ব্রেতোঁ বলতেন, ‘ভাবনার যথাযথ পদ্ধতি অনুধাবনের জন্যে সুররিয়ালিজম আবশ্যক।’ এ ধারায় স্বপ্ন ও বাস্তবতার মিশ্রণ হয় বলে সুররিয়ালিজমকে স্বপ্নবাস্তবতাও বলা হয়ে থাকে।
সুররিয়ালিজমের ঢেউ খুব অল্প সময়েই শিল্পের সবগুলো শাখায় আছড়ে পড়ে। কবিতা, গান থেকে শুরু করে নাটক, সিনেমা পর্যন্ত সুররিয়ালিস্টদের চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। ১৯২৪ সাল থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত সুররিয়ালিজম ধারায় অন্তত ছয়টি সিনেমা নির্মিত হয়। এ ধারার প্রধান শিল্পীরা হলেন জ্যাঁ আর্প, ম্যাক্স আর্নেস্ট, আঁদ্রে মেসন, সালভাদর দালি, রেনে ম্যাগরেট, পিয়েরো রয়, জোয়ান মিরো, পল ডেলভাক্স, ফ্রিদা কাহলো প্রমুখ। এ ধারার চিত্রকর্মের মধ্যে ১৯৩১ সালে আঁকা সালভাদর দালির ‘দ্য পারসিসটেন্স অব মেমোরি’ সবচেয়ে আলোচিত ছবি। এটি কেবল এ ধারার মধ্যেই আলোচিত চিত্রকর্মই নয়, এটি দালিরও অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিভার নিদর্শন। ‘দ্য পারসিসটেন্স অব মেমোরি’-তে দালি ‘সময়ের’ বিচিত্র অবস্থাকে ফ্রেমবন্দি করতে চেষ্টা করেছেন। ‘মেটামরফসিস অব নার্সিসাস’, ‘নভিলিটি অব টাইম’, ‘প্রোফাইল অব টাইম’ প্রভৃতি তাঁর গুরুত্বপূর্ণ কাজ।
সুররিয়ালিজম ধারার প্রধানতম চিত্রকর্মের মধ্যে রেনে ম্যাগরেটের ‘দ্য সন অব ম্যান’, ‘দিস ইজ নট এ পাইপ’, জর্জিও দি চিরিকো-এর ‘দ্য রেড টাওয়ার’, ম্যাক্স আর্নেস্টের ‘দি এলিফ্যান্ট সিলিবেস’, ইভ তঁগির ‘রিপ্লাই টু রেড’ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে সুররিয়ালিজম আন্দোলন থেমে যায়। শিল্পবোদ্ধারা মনে করেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষের মধ্য দিয়ে এ আন্দোলনটির অনানুষ্ঠানিক মৃত্যু ঘটে। কিন্তু অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আন্দোলনের মতো সুররিয়ালিজমের চর্চা বর্তমানেও হচ্ছে। বাংলাদেশের শিল্পাঙ্গনেও সুররিয়ালিজমের প্রভাব লক্ষ করা যায়। ১৯২৪ সালে প্রকাশ করেন তাঁর প্রথম সুররিয়ালিস্ট ম্যানিফেস্টো । মার্কসবাদের সঙ্গে আর্তুর র্যাঁবোর আত্মপরিবর্তনের ভাবনাকে একত্রিত করার উদ্দেশে ব্রেতঁ ১৯২৭ সালে ফরাসি কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন । কিন্তু সাম্যবাদীদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বেশিদিন টেকেনি । সেখান থেকেও তিনি ১৯৩৩ সালে বিতাড়িত হন । পরাবাস্তববাদীদের “উন্মাদ প্রেম” তত্বটি ব্রেতঁর এবং “উন্মাদ প্রেম” করার জন্য বেশ কিছু তরুণী সুররিয়ালিস্টদের প্রতি আকৃষ্ট হন । যৌনতার স্বেচ্ছাচারিতার ঢেউ ওঠে সাহিত্যিক ও শিল্পী মহলে ; পরাবাস্তববাদীদের নামের সঙ্গে একজন বা বেশি নারীর সম্পর্ক ঘটে এবং সেই নারীরা তাঁদের পুরুষ প্রেমিকদের নামেই খ্যাতি পেয়েছেন ।
তাঁর রাজনৈতিক টানাপোড়েন এবং অন্যান্য কারণে প্রেভের, বারোঁ, দেসনস, লেইরিস, লিমবোর, মাসোঁ, কোয়েন্যু, মোরিস, বোইফার সম্পর্কচ্ছদ করেন ব্রেতঁর সঙ্গে এবং গেয়র্গে বাতাইয়ের নেতৃত্বে পৃথক গোষ্ঠী তৈরি করেন । এই সময়েই, ১৯২৯ নাগাদ, ব্রেতঁর গোষ্ঠীতে যোগ দেন সালভাদর দালি, লুই বুনুয়েল, আলবের্তো জিয়াকোমেত্তি, রেনে শার এবং লি মিলার । ত্রিস্তঁ জারার সঙ্গে ঝগড়া মিটমাট করে নেন ব্রেতঁ । দ্বিতীয় সুররিয়ালিস্ট ইশতাহার প্রকাশের সময়ে তাতে সই করেছিলেন আরাগঁ, আর্নস্ট, বুনুয়েল, শার, ক্রেভাল, দালি, এলুয়ার, পেরে, টাঙ্গুই, জারা, ম্যাক্সিম আলেকজান্দ্রে, জো বনসকোয়েত, কামিলে গোয়েমানস, পল নুগ, ফ্রান্সিস পোঙ্গে, মার্কো রিসটিচ, জর্জ শাদুল, আঁদ্রে তিরিয়ঁ এবং আলবেয়ার ভালেনতিন । ফেদেরিকো গারথিয়া লোরকা বন্ধু ছিলেন সালভাদর দালি এবং লুই বুনুয়েলের, আলোচনায় অংশ নিতেন, কিন্তু সুররিয়ালিস্ট গোষ্ঠিতে যোগ দেননি । ১৯২৯ সালে তাঁর মনে হয়েছিল যে দালি আর বুনুয়েলের ফিল্ম “একটি আন্দালুসিয় কুকুর” তাঁকে আক্রমণ করার জন্যে তৈরি হয়েছিল ; সেই থেকে তিনি সুররিয়ালিস্টদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন । আরাগঁ ও জর্জ শাদুল ব্রেতঁ’র গোষ্ঠী ত্যাগ করেছিলেন রাজনৈতিক মতভেদের কারণে, যদিও ব্রেতঁ বলতেন যে তিনিই ওনাদের তাড়িয়েছেন ।
১৯৩০ সালে কয়েকজন পরাবাস্তববাদী আঁদ্রে ব্রেতঁ’র একচেটিয়া নেতৃত্বে বিরক্ত হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে একটি প্যামফ্লেট ছাপিয়েছিলেন । পরাবাস্তববাদ আন্দোলন দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় । ১৯৩৫ সালে ব্রেতঁ এবং সোভিয়েত লেখক ও সাংবাদিক ইলিয়া এরেনবার্গের মাঝে ঝগড়া এমন স্তরে গিয়ে পৌঁছোয় যে প্যারিসের রাস্তায় তাঁদের দুজনের হাতাহাতি আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল । এরেনবার্গ একটি পুস্তিকা ছাপিয়ে বলেছিলেন যে পরাবাস্তববাদীরা পায়ুকামী । এর ফলে পরাবাস্তববাদীদের ইনটারন্যাশানাল কংগ্রেস ফর দি ডেফেন্স অফ কালচার সংস্হা থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল । সালভাদর দালি বলেছিলেন যে পরাবাস্তববাদীদের মধ্যে প্রকৃত সাম্যবাদী হলেন একমাত্র রেনে ক্রেভাল । চটে গিয়ে ক্রেভালকে পরাবাস্তববাদী আন্দোলন থেকে বের করে দ্যান ব্রেতঁ । অঁতনা অতো, ভিত্রাক এবং সুপোকে পরাবাস্তববাদী দল থেকে বের করে দ্যান ব্রেতঁ, মূলত সাম্যবাদের প্রতি ব্রেতঁর আত্মসমর্পণের কারণে এই তিনজন বিরক্ত বোধ করেন ।
১৯৩৮ সালে ব্রেতঁ মেকসিকো যাবার সুযোগ পান এবং লিও ট্রটস্কির সঙ্গে দেখা করেন । তাঁর সঙ্গে ছিলেন দিয়েগো রিভেরা ও ফ্রিদা কালহো । ট্রটস্কি এবং ব্রেতঁ একটা যুক্ত ইশতাহার প্রকাশ করেছিলেন, “শিল্পের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা” শিরোনামে । লুই আরাগঁর সঙ্গেও ব্রেতঁর সম্পর্ক ভালো ছিল না । ১৯১৯ থেকে ১৯২৪ পর্যন্ত ডাডাবাদীদের সঙ্গে আন্দোলন করার পর ১৯২৪ সালে আরাগঁ যোগ দেন পরাবাস্তববাদী আন্দোলনে । অন্যান্য ফরাসী পরাবাস্তববাদীদের সঙ্গে তিনিও ফরাসি কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দ্যান এবং পার্টির পত্রিকায় কলাম ও রাজনৈতিক কবিতা লিখতেন । আরাগঁর সঙ্গে ব্রেতঁর বিবাদের কারণ হল ব্রেতঁ চেয়েছিলেন ট্রটস্কির সঙ্গী ভিকতর সার্জকে সন্মানিত করতে । পরবর্তীকালে, ১৯৫৬ নাগাদ, সোভিয়েত রাষ্ট্র সম্পর্কে নিরাশ হন আরাগঁ, বিশেষ করে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির বিংশ কংগ্রেসের পর যখন নিকিতা ক্রুশ্চভ আক্রমণ করেন জোসেফ স্তালিনের ব্যক্তিত্ববাদকে । তা সত্ত্বেও স্তালিনপন্হী আরাগঁ ও ট্রটস্কিপন্হী ব্রেতঁর কখনও মিটমাট হয়নি । কাট-আপ কবিতার জনক ব্রায়ন জিসিনকেও গোষ্ঠী থেকে বিতাড়ন করেন ব্রেতঁ ; ব্রায়ান জিসিনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ছিলেন বিট ঔপন্যাসিক উইলিয়াম বারোজ । বিট আন্দোলনের প্রায় সকলেই সুররিয়ালিজম দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন । বিটদের যৌন স্বাধীনতার ভাবনা-চিন্তায় সুররিয়ালিস্টদের অবদান আছে ।
পরাবাস্তববাদই সম্ভবত প্রথম কোনো গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন, যেখানে নারীকে দূরতম কোনো নক্ষত্রের আলোর মতো, প্রেরণা ও পরিত্রাণের মতো, কল্পনার দেবী প্রতিমার মতো পবিত্র এক অবস্থান দেওয়া হয়েছিল। নারী তাদের চোখে একই সঙ্গে পবিত্র কুমারী, দেবদূত আবার একই সঙ্গে মোহিনী জাদুকরী, ইন্দ্রিয় উদ্দীপক ও নিয়তির মতো অপ্রতিরোধ্য। ১৯২৯ সালে দ্বিতীয় সুররিয়ালিস্ট ম্যানিফেস্টোয় আদ্রেঁ ব্রেতঁ নারীকে এরকম একটি অপার্থিব অসীম স্বপ্নিল চোখে দেখা ও দেখানোর চেষ্টা করেছিলেন। পুরুষ শিল্পীদের প্রেরণা, উদ্দীপনা ও কল্পনার সুদীর্ঘ সাম্পান হয়ে এগিয়ে আসবেন নারীরা। হয়ে উঠবেন পুরুষদের আরাধ্য ‘মিউজ’ আর একই সঙ্গে femme fatale। সুদৃশ্য উঁচু পূজার বেদি উদ্ভাসিত করে যেখানে বসে থাকবেন নারীরা। তাঁদের স্বর্গীয় প্রাসাদে আরো সৃষ্টিশীল হয়ে উঠবে পুরুষ।
ব্রেতঁ ছিলেন সেই সময়ের কবিতার অন্যতম প্রধান পুরুষ। তাঁর সম্মোহক ব্যক্তিত্বে আচ্ছন্ন হননি তাঁর সান্নিধ্যে এসেও – এরকম কোনো দৃষ্টান্ত কোথাও নেই। উজ্জ্বল, সাবলীল, মেধাবী, স্বতঃস্ফূর্ত এবং নায়কসুলভ ব্রেতঁ একই সঙ্গে ছিলেন উদ্ধত, আক্রমণাত্মক ও অহমিকাপূর্ণ। নিজের তাত্ত্বিক অবস্থান থেকে মাঝেমধ্যেই ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে যেতেন। কিন্তু যদি তাঁর একবার মনে হতো যে কেউ তাঁর প্রভুত্বকে অগ্রাহ্য করছে, সর্বশক্তি দিয়ে তাকে আঘাত করতেন। নেতৃত্ব দেওয়ার সব গুণ প্রকৃতিগতভাবেই ছিল তাঁর মধ্যে। মহিলাদের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার ছিল তরুণ প্রেমিকের মতো সম্ভ্রমপূর্ণ। তাঁর আকর্ষণীয় বাচনভঙ্গি, অভিজাত ভাষা – এসবের সঙ্গে মাঝেমধ্যেই মেজাজ হারিয়ে সম্পূর্ণ লাগামহীন হয়ে পড়া আর দুর্বোধ্য জটিল মানসিকতার জন্য পারতপক্ষে অনেকেই ঘাঁটাতে চাইতেন না তাঁকে।
নারী পরাবাস্তববাদীদের সংখ্যা কম ছিল না । কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে উল্লেখ্য ফ্রিদা কাহলো, আসে বার্গ, লিজে দেহামে, আইরিন হামোয়ের, জয়েস মানসোর, ওলগা ওরোজকো, আলেহান্দ্রা পিৎসারনিক, ভ্যালেনটিন পেনরোজ, জিসেল প্রাসিনস, ব্লাঙ্কা ভারেলা, ইউনিকা জুর্ন প্রমুখ । নারী চিত্রকররা সংখ্যায় ছিলেন বেশি । তাঁদের মধ্যে উল্লেখ্য গেরট্রুড আবেরকমবি, মারিয়ন আদনামস, আইলিন ফরেসটার আগার, রাশেল বায়েস, ফ্যানি ব্রেনান, এমি ব্রিজওয়াটার, লেনোরা ক্যারিংটন, ইথেল কলকুহুন, লেনোর ফিনি, জেন গ্রাভেরোল, ভ্যালেনটিন য়োগো, ফ্রিদা খাহলো, রিটা কার্ন-লারসেন, গ্রেটা নুটসন ( ত্রিস্তঁ জারার স্ত্রী ), জাকেলিন লামবা ( আঁদ্রে ব্রেতঁ’র স্ত্রী), মারুহা মালো, মার্গারেট মডলিন, গ্রেস পেইলথর্প, অ্যালিস রাহোন, এডিথ রিমিঙটন, পেনিলোপি রোজমন্ট, কে সেজ ( ইভস তাঙ্গুইর স্ত্রী ), ইভা স্বাঙ্কমাজেরোভা, ডরোথি ট্যানিঙ ( ম্যাক্স আর্নস্টের স্ত্রী ), রেমেদিওস ভারো ( বেনিয়ামিন পেরের স্ত্রী ) প্রমুখ । ভাস্করদের মধ্যে উল্লেখ্য এলিজা ব্রেতঁ ( আঁদ্রে ব্রেতঁ’র তৃতীয় স্ত্রী ), মেরে ওপেনহাইম ( মান রে’র মডেল ছিলেন ) এবং মিমি পারেন্ট । ফোটোগ্রাফারদের মধ্যে উল্লেখ্য ছিলেন ক্লদ কাহুন, নুশ এলুয়ার, হেনরিয়েতা গ্রিনদাত, আইডা কার, দোরা মার ( পাবলো পিকাসোর সঙ্গে নয় বছর লিভ টুগেদার করেছিলেন ), এমিলা মেদকোভা, লি মিলার, কাতি হোরনা প্রমুখ । পুরুষ পরাবাস্তববাদীদের বহু ফোটো এই নারী ফোটোগ্রাফারদের কারণেই ইতিহাসে স্হান পেয়েছে ।
নারীদের নিয়ে পরাবাস্তববাদীদের এই স্বপ্নিল কাব্যময় উচ্ছ্বাস জোরালো একটা ধাক্কা খেল যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পশ্চিম ইউরোপে দ্রম্নত বদলাতে থাকা পরিস্থিতির ভস্ম ও শোণিত স্নাত শোণিত আত্মশক্তিসম্পন্ন নারীরা তাঁদের ভারী বাস্তবতা নিয়ে এসে দাঁড়ালেন সামনে। স্বপ্নে দেখা নারীর আয়না-শরীর ভেঙে পড়ল ঝুরঝুর করে আর বেরিয়ে এলো মেরুদ-সম্পন্ন রক্তমাংসের মানবী। সুররিয়ালিজম চেয়েছিল পুরুষের নিয়ন্ত্রণে নারীদের মুক্তি। কিন্তু যে গভীর অতলশায়ী মুক্তি দরজা খুলে দিলো নারীদের জন্য, সুররিয়ালিজম তার জন্য তৈরি ছিল না। মৃত অ্যালবাট্রসের মতো এই বিমূর্ত আদর্শায়িত ধারণা নারী শিল্পীদের গলায় ঝুলে থেকেছে, যাকে ঝেড়ে ফেলে নিজস্ব শিল্পসত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করা দুঃসাধ্য ছিল। সময় লেগেছে সাফল্য পেতে। কিন্তু দিনের শেষে হেসেছিলেন তাঁরাই। এমন নয় যে, পরাবাস্তবতার প্রধান মশালবাহক ব্রেতঁ চাইছিলেন যে পুরুষরাই হবেন এই আন্দোলনের ঋত্বিক আর দ্যুতিময় নারী শিল্পী এবং সাহিত্যিকদের কাজ হবে মুগ্ধ সাদা পালক ঘাসের ওপরে ফেলে যাওয়া এবং আকর্ষণীয় ‘গুজব’ হিসেবে সুখী থাকা। ১৯২৯ সালে দ্বিতীয় সুররিয়ালিস্ট ম্যানিফেস্টো প্রকাশের পরবর্তী প্রদর্শনীগুলোতে নারী শিল্পীরা সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন ঠিকই। কিন্তু পুরুষ উদ্ভাবিত পরাবাস্তবতা থেকে তাঁদের ভাষা, স্বর ও দৃষ্টিভঙ্গি ছিল স্বতন্ত্র। নিজেদের ভারী অসিত্মত্ব, শরীরী উপস্থিতি জোরালোভাবে জায়গা পেল তাঁদের ছবিতে।
কিন্তু নারী শিল্পীদের কাছে আত্মপ্রতিকৃতি হয়ে উঠল একটি সশস্ত্র ভাষার মতো। নিজস্ব গোপন একটি সন্ত্রাসের মতো। এই আন্দোলনের মধ্যে নারীরা এমন এক পৃথিবীর ঝলক দেখলেন, যেখানে আরোপিত বিধিনিষেধ না মেনে সৃজনশীল থাকা যায়, দমচাপা প্রতিবাদের ইচ্ছেগুলোর উৎস থেকে পাথরের বাঁধ সরিয়ে দেওয়া যায়। নগ্ন ও উদ্দাম করা যায় কল্পনাকে। নোঙর নামানো জাহাজের মতো অনড় ও ঠাসবুনট একটি উপস্থিতি হয়ে ছবিতে নিজের মুখ তাঁদের কাছে হয়ে উঠল অন্যতম প্রধান আইকন। যে ছবি আত্মপ্রতিকৃতি নয়, সেখানেও বারবার আসতে থাকল শিল্পীর শরীরী প্রতিমা। ফ্রিদা কাহ্লোর (১৯০৭-৫৪) ক্যানভাস তাঁর যন্ত্রণাবিদ্ধ শান্ত মুখশ্রী ধরে রাখল। মুখের বিশেষ কিছু চিহ্ন যা তাঁকে চেনায় – যেমন পাখির ডানার মতো ভুরু, আমন্ড আকারের চোখ ছবিতেও আনলেন তিনি। রিমেদিওস ভারোর (১৯০৮-৬৩) ছবিতে পানপাতার মতো মুখ, তীক্ষন নাক, দীর্ঘ মাথাভর্তি চুলের নারীর মধ্যে নির্ভুল চেনা গেল শিল্পীকে। আবার লিওনর ফিনির (১৯১৮-৯৬) আঁকা নারীরা তাদের বেড়ালের মতো কালো চোখ আর ইন্দ্রিয়াসক্ত মুখ নিয়ে হয়ে উঠল ফিনিরই চেনা মুখচ্ছবি। ১৯৩৯ সালের ‘The Alcove : An interior with three women’ ছবিতে ভারী পর্দা টাঙানো ঘরে দুজন অর্ধশায়িত মহিলা পরস্পরকে ছুঁয়ে আছেন। আর একজন মহিলা দাঁড়িয়ে। তিনজনেই যেন কোনো কিছুর প্রতীক্ষা করছেন চাপা উদ্বিগ্ন মুখে। যে তিনজন নারীর ছবি, তাঁরা যে লিওনর ফিনি, লিওনারা ক্যারিংটন এবং ইলিন অগার – এটা ছবিটিকে একঝলক দেখেই চেনা যায়। এমনকি যখন অন্য কোনো নারীর প্রতিকৃতি আঁকছেন তাঁরা, সেখানেও তাঁদের বিদ্রোহের অস্বীকারের জোরালো পাঞ্জার ছাপ এই শিল্পীরা সেইসব নারীর মুখে ঘন লাল নিম্নরেখা দিয়ে বুঝিয়ে দিতেন
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হতে ১৯৩৯ সালে অধিকাংশ পরাবাস্তববাদী বিদেশে পালিয়ে যান এবং তাঁদের মধ্যে আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও বক্তব্য নিয়ে খেয়োখেয়ি বেধে যায় । অলোচকরা মনে করেন যে গোষ্ঠী হিসাবে পরাবাস্তববাদ ১৯৪৭ সালে ভেঙে যায়, প্যারিসে “লে সুররিয়ালিজমে” প্রদর্শনীর পর । যুদ্ধের শেষে, প্যারিসে ব্রেতঁ ও মার্সেল দ্যুশঁ’র ফিরে আসার পর প্রদর্শনীর কর্তারা সম্বর্ধনা দিতে চাইছিলেন কিন্তু পুরোনো পরাবাস্তববাদীরা জানতে পারলেন যে একদল যুবক পরাবাস্তববাদীর আবির্ভাব হয়েছে, যাঁরা বেশ ভিন্ন পথ ধরে এগোতে চাইছেন । যুবকদের মধ্যে উল্লেখ্য ছিলেন ফ্রাঁসিস বেকঁ, আলান দাভি, এদুয়ার্দো পোলোৎসি, রিচার্ড হ্যামিলটন প্রমুখ ।
সুররিয়ালিজমের উদ্ভব সত্ত্বেও ডাডার প্রভাব কিন্তু ফুরিয়ে যায়নি, তা প্রতিটি দশকে কবর থেকে লাফিয়ে ওঠে, যেমন আর্পের বিমূর্ততা, শুইটারের নির্মাণ, পিকাবিয়ার টারগেট ও স্ট্রাইপ এবং দ্যুশঁ’র রেডিমেড বস্তু বিশ শতকের শিল্পীদের কাজে ও আন্দোলনে ছড়িয়ে পড়ছিল । স্টুয়ার্ট ডেভিসের বিমূর্ততা থেকে অ্যান্ডি ওয়ারহলের পপ আর্ট, জাসপার জনসের টারগেট ও ফ্ল্যাগ থেকে রবার্ট রাউশেনবার্গের কোলাঝে -- সমসাময়িক সাহিত্য ও শিল্পের যেদিকেই তাকানো হোক পাওয়া যাবে ডাডার প্রভাব, সুররিয়ালিজমের উপস্হিতি । ১৯৬৬ সালে মৃত্যুর আগে, ব্রেতঁ লিখেছিলেন, “ডাডা আন্দোলনের পর আমরা মৌলিক কিছু করিনি । ডাডা ও সুররিয়ালিজম আন্দোলনকারীদের ওপর প্রচুর চাপ সৃষ্টি করেছিল এবং কয়েকজন আত্মহত্যা করেন, যেমন জাক রিগো, রেনে ক্রেভেল, আরশাইল গোর্কি, অসকার দোমিংগেজ প্রমুখ । অত্যধিক মাদক সেবনে মৃত্যু হয় গিলবার্ত লেকঁতে ও অঁতনা আতোর ।
 মলয় রায়চৌধুরী | 122.179.172.247 | ২৪ আগস্ট ২০২১ ১৯:২০734896
মলয় রায়চৌধুরী | 122.179.172.247 | ২৪ আগস্ট ২০২১ ১৯:২০734896হাংরি আন্দোলন : এক সাহিত্যক উথালপাথাল যা অনেকে সহ্য করতে পারেন না
মলয় রায়চৌধুরী
এক
চুঁচুড়া-নিবাসী মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী আমাকে জিগ্যেস করেছেন, “আপনাদের চিন্তাধারা যখন প্রবলভাবে সক্রিয়, তখন আমি কলেজ স্টুডেন্ট, ইংরেজিতে অনার্স সরকারি কলেজ, বাঘা বাঘা অধ্যাপক, কিন্তু তাঁরা কেউ হাংরি আন্দোলন সম্পর্কে একটি কথাও উচ্চারণ করেন নি। গ্রামের ছেলে, ইংরাজি ভালো বুঝতাম না বলে বাংলার ক্লাসে গিয়ে আধুনিক কবিতা, তারপরের ট্রেন্ড সম্পর্কে কত কথা শুনলাম কিন্তু হাংরি আন্দোলন ----- মলয় রায়চৌধুরী, শম্ভু রক্ষিত, শৈলেশ্বর, সুভাষের নাম একবারও উচ্চারিত হ'তে শুনিনি। হ্যাঁ, স্যার, যদিও এখন আমার ষাট বছর বয়স কিন্তু স্মৃতিশক্তি ভালো আছে। আমি স্কুল শিক্ষক, আর ২৩ দিন বাকি আছে। স্কুলপাঠ্য একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসেও আপনাদের নাম এবং অবদানের কথা লেখা নেই, অথচ পড়তে পড়তে জানতে পারলাম আপনার লেখার ওপর গবেষণা করে অনেকে পি.এইচ.ডি. করেছেন।”
মৃত্যুঞ্জয় যে প্রশ্ন তুলেছেন তা অনেকেরই । তা হল হাংরি আন্দোলন সম্পর্কে বিদ্যায়তনিক ভীতি ; মধ্যবিত্ত মূল্যবোধ আক্রান্ত হবার আতঙ্ক । অথচ কয়েকটা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা হয়েছে, কেবল পশ্চিমবাংলায় নয়, অন্যান্য ভাষাতেও, যেমন জার্মানিতে ড্যানিয়েলা লিমোনেলা করেছেন, আমেরিকায় ওয়েসলিয়ান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে করেছেন মারিনা রেজা । অবশ্য হাংরি আন্দোলন তবুও আলোচিত হয়, কিন্তু শ্রুতি, শাস্ত্রবিরোধী, নিমসাহিত্য একেবারেই আলোচিত হয় না ।
হাংরি আন্দোলনকারীদের নিজেদের মধ্যে সম্পর্কের অবনতিও একটা কারণ, বিশেষ করে হাংরি মামলায় কয়েকজন রাজসাক্ষী হবার পর । উত্তরবঙ্গে হাংরি জেনারেশনের প্রসার সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে, হাংরি পত্রিকা ‘কনসেনট্রেশন ক্যাম্প’ এর সম্পাদক অলোক গোস্বামী এই কথাগুলো লিখেছিলেন, তা থেকে যৎসামান্য আইডিয়া হবে :-
“নব্বুই দশকে সদ্য প্রকাশিত কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প বগলে নিয়ে এক ঠা ঠা দুপুরে আমি হাজির হয়েছিলাম শৈলেশ্বরের বাড়ির গেটে। একা। ইচ্ছে ছিল শৈলেশ্বরের সঙ্গে মুখোমুখি বসে যাবতীয় ভুল বোঝাবুঝি নিয়ে খোলাখুলি কথা বলবো। যেহেতু স্মরণে ছিল শৈলেশ্বরের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের স্মৃতি তাই আস্থা ছিল শৈলেশ্বরের প্রজ্ঞা,ব্যক্তিত্ব,যুক্তিবোধ তথা ভদ্রতাবোধের ওপর। দৃঢ় বিশ্বাস ছিল শৈলেশ্বর আমাদের ভুলগুলো ধরিয়ে দেবেন এবং যৌথ আলোচনাই পারবে সব ভুল বোঝাবুঝি মিটিয়ে নতুন উদ্যমে একসাথে পথ চলা শুরু করতে। কিন্তু দুভার্গ্য বশতঃ তেমন কিছু ঘটলো না। বেল বাজাতেই গেটের ওপারে শৈলেশ্বর। আমাকে দেখেই ভ্রূ কুঁচকে ফেললেন।
--কী চাই!
মিনমিন করে বললাম, আপনার সঙ্গে কথা বলবো।
--কে আপনি?
এক এবং দুই নম্বর প্রশ্নের ভুল অবস্থান দেখে হাসি পাওয়া সত্বেও চেপে গিয়ে নাম বললাম।
--কি কথা?
--গেটটা না খুললে কথা বলি কিভাবে!
--কোনো কথার প্রয়োজন নেই। চলে যান।
--এভাবে কথা বলছেন কেন?
--যা বলছি ঠিক বলছি। যান। নাহলে কিন্তু প্রতিবেশীদের ডাকতে বাধ্য হবো।
এরপর স্বাভাবিক কারণেই খানিকটা ভয় পেয়েছিলাম কারণ আমার চেহারাটা যেরকম তাতে শৈলেশ্বর যদি একবার ডাকাত, ডাকাত বলে চেঁচিয়ে ওঠেন তাহলে হয়ত জান নিয়ে ফেরার সুযোগ পাবো না। তবে 'ছেলেধরা' বলে চেল্লালে ভয় পেতাম না। সমকামিতার দোষ না থাকায় নির্ঘাত রুখে দাঁড়াতাম।
ভয় পাচ্ছি অথচ চলেও যেতে পারছি না। সিদ্ধান্তে পৌঁছতে গেলে আরও খানিকটা জানা বোঝা জরুরি।
--ঠিক আছে, চলে যাচ্ছি। তবে পত্রিকার নতুন সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে সেটা রাখুন।
এগিয়ে আসতে গিয়েও থমকে দাঁড়ালেন শৈলেশ্বর।
--কোন পত্রিকা?
--কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প।
--নেব না। যান।
এরপর আর দাঁড়াইনি। দাঁড়ানোর প্রয়োজনও ছিল না। ততক্ষণে বুঝে ফেলেছি ব্যক্তি শৈলেশ্বর ঘোষকে চিনতে ভুল হয়নি আমাদের। আর এই সমঝদারি এতটাই তৃপ্তি দিয়েছিল যে অপমানবোধ স্পর্শ করারই সুযোগ পায়নি।”
এরকম দুর্ব্যবহার সাহিত্য ও চিত্র আন্দোলনে নতুন কিছু নয় । পরাবাস্তববাদ আন্দোলনে আঁদ্রে ব্রেতঁর সঙ্গে অনেকের সম্পর্ক ভালো ছিল না, দল বহুবার ভাগাভাগি হয়েছিল, অথচ সেসব নিয়ে বাঙালি আলোচকরা তেমন উৎসাহিত নন, যতোটা হাংরি আন্দোলনের দল-ভাগাভাগি নিয়ে । দুই
১৯৫৯-৬০ সালে আমি দুটি লেখা নিয়ে কাজ করছিলুম। একটি হল ইতিহাসের দর্শন যা পরে বিংশ শতাব্দী পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়েছিল। অন্যটি মার্কসবাদের উত্তরাধিকার যা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। এই দুটো লেখা নিয়ে কাজ করার সময়ে হাংরি আন্দোলনের প্রয়োজনটা আমার মাথায় আসে । হাংরি আন্দোলনের ‘হাংরি’ শব্দটি আমি পেয়েছিলুম ইংরেজ কবি জিওফ্রে চসারের ইন দি সাওয়ার হাংরি টাইম বাক্যটি থেকে। ওই সময়ে, ১৯৬১ সালে, আমার মনে হয়েছিল যে স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে জাতীয়তাবাদী নেতারা যে সুখী, সমৃদ্ধ, উন্নত ভারতবর্ষের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন, তা টকে গিয়ে পচতে শুরু করেছে উত্তর ঔপনিবেশিক কালখন্ডে।
উপরোক্ত রচনাদুটির খসড়া লেখার সময়ে আমার নজরে পড়েছিল ওসওয়াল্ড স্পেংলারের লেখা দি ডিক্লাইন অব দি ওয়েষ্ট বইটি, যার মূল বক্তব্য থেকে আমি গড়ে তুলেছিলুম আন্দোলনের দার্শনিক প্রেক্ষিত। ১৯৬০ সালে আমি একুশ বছরের ছিলুম। স্পেংলার বলেছিলেন যে একটি সংস্কৃতির ইতিহাস কেবল একটি সরলরেখা বরাবর যায় না, তা একযোগে বিভিন্ন দিকে প্রসারিত হয়; তা হল জৈবপ্রক্রিয়া, এবং সেকারণে সমাজটির নানা অংশের কার কোন দিকে বাঁকবদল ঘটবে তা আগাম বলা যায় না। যখন কেবল নিজের সৃজনক্ষমতার ওপর নির্ভর করে তখন সংস্কৃতিটি নিজেকে বিকশিত ও সমৃদ্ধ করতে থাকে, তার নিত্যনতুন স্ফুরণ ও প্রসারণ ঘটতে থাকে। কিন্তু একটি সংস্কৃতির অবসান সেই সময়ে আরম্ভ হয় যখন তার নিজের সৃজনক্ষমতা ফুরিয়ে গিয়ে তা বাইরে থেকে যা পায় তাই আত্মসাৎ করতে থাকে, খেতে থাকে, তার ক্ষুধা তৃপ্তিহীন। আমার মনে হয়েছিল যে দেশভাগের ফলে পশ্চিমবঙ্গ এই ভয়ংকর অবসানের মুখে পড়েছে, এবং উনিশ শতকের মনীষীদের পর্যায়ের বাঙালির আবির্ভাব আর সম্ভব নয়। এখানে বলা ভালো যে আমি কলাকাতার আদি নিবাসী পরিবার সাবর্ণ চৌধুরীদের বংশজ, এবং সেজন্যে বহু ব্যাপার আমার নজরে যেভাবে খোলসা হয় তা অন্যান্য লেখকদের ক্ষেত্রে সম্ভব নয়।
ওই চিন্তা ভাবনার দরুণ আমার মনে হয়েছিল যে কিঞ্চিদধিক হলেও, এমনকি যদি ডিরোজিওর পর্যায়েও না হয়, তবু হস্তক্ষেপ দরকার, আওয়াজ তোলা দরকার, আন্দোলন প্রয়োজন। আমি আমার বন্ধু দেবী রায়কে, দাদা সমীর রায়চৌধুরীকে, দাদার বন্ধু শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে আমার আইডিয়া ব্যাখ্যা করি, এবং প্রস্তাব দিই হাংরি নামে আমরা একটা আন্দোলন আরম্ভ করব। ১৯৫৯ থেকে টানা দুবছরের বেশি সে সময়ে শক্তি চট্টোপাধ্যায় দাদার চাইবাসার বাড়িতে থাকতেন। দাদার চাইবাসার বাড়ি, যা ছিল নিমডি নামে এক সাঁওতাল-হো অধ্যুষিত গ্রামের পাহাড় টিলার ওপর, সে-সময়ে হয়ে উঠেছিল তরুণ শিল্পী-সাহিত্যিকদের আড্ডা। ১৯৬১ সালে যখন হাংরি আন্দোলনের প্রথম বুলেটিন প্রকাশিত হয়, এবং ১৯৬২ সালে বেশ কয়েক মাস পর্যন্ত, আমরা এই চারজনই ছিলুম আন্দোলনের নিউক্লিয়াস।
ইউরোপের শিল্প-সাহিত্য আন্দোলনগুলো সংঘটিত হয়েছিল একরৈখিক ইতিহাসের বনেদের ওপর অর্থাৎ আন্দোলনগুলো ছিল টাইম-স্পেসিফিক বা সময় কেন্দ্রিক। কল্লোল গোষ্ঠী এবং কৃত্তিবাস গোষ্ঠী তাঁদের ডিসকোর্সে যে নবায়ন এনেছিলেন সে কাজগুলোও ছিল কলোনিয়াল ইসথেটিক রিয়্যালিটি বা ঔপনিবেশিক নন্দন-বাস্তবতার চৌহদ্দির মধ্যে, কেননা সেগুলো ছিল যুক্তিগ্রন্থনা নির্ভর এবং তাদের মনোবীজে অনুমিত ছিল যে ব্যক্তিপ্রতিস্বের চেতনা ব্যাপারটি একক, নিটোল ও সমন্বিত। সময়ানুক্রমী ভাবকল্পের প্রধান গলদ হল যে তার সন্দর্ভগুলো নিজেদের পূর্বপুরুষদের তুলনায় উন্নত মনে করে, এবং স্থানিকতাকে ও অনুস্তরীয় আস্ফালনকে অবহেলা করে।
১৯৬১ সালের প্রথম বুলেটিন থেকেই হাংরি আন্দোলন চেষ্টা করল সময়তাড়িত চিন্তাতন্দ্র থেকে সম্পূর্ণ পৃথক পরিসরলব্ধ চিন্তাতন্ত্র গড়ে তুলতে। সময়ানুক্রমী ভাবকল্পে যে বীজ লুকিয়ে থাকে, তা যৌথতাকে বিপন্ন আর বিমূর্ত করার মাধ্যমে যে মননসন্ত্রাস তৈরি করে, তার দরুন প্রজ্ঞাকে যেহেতু কৌমনিরপেক্ষ ব্যক্তিলক্ষণ হিসেবে প্রতিষ্ঠা দেয়া হয়, সমাজের সুফল আত্মসাৎ করার প্রবণতায় ব্যক্তিদের মাঝে ইতিহাসগত স্থানাঙ্ক নির্ণয়ের হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে ব্যক্তিক তত্ত্বসৌধ নির্মাণ। ঠিক এই জন্যেই, ইউরোপীয় শিল্পসাহিত্য আন্দোলনগুলো খতিয়ে যাচাই করলে দেখা যাবে যে ব্যক্তিপ্রজ্ঞার আধিপত্যের দামামায় সমাজের কান ফেটে এমন রক্তাক্ত যে সমাজের পাত্তাই নেই কোন। কৃত্তিবাস গোষ্ঠীর দিকে তাকালে দেখব যে পুঁজিবলবান প্রাতিষ্ঠানিকতার দাপটে এবং প্রতিযোগী ব্যক্তিবাদের লালনে সমসাময়িক শতভিষা গোষ্ঠী যেন অস্তিত্বহীন। এমনকি কৃত্তিবাস গোষ্ঠীও সীমিত হয়ে গেছে দুতিনজন মেধাস্বত্বাধিকারীর নামে। পক্ষান্তরে, আমরা যদি ঔপনিবেশিক নন্দনতন্ত্রের আগেকার প্রাকঔপনিবেশিক ডিসকোর্সের কথা ভাবি, তাহলে দেখব যে পদাবলী সাহিত্য নামক স্পেস বা পরিসরে সংকুলান ঘটেছে বৈষ্ণব ও শাক্ত কাজ; মঙ্গলকাব্য নামক-ম্যাক্রো-পরিসরে পাবো মনসা বা চন্ডী বা শিব বা কালিকা বা শীতলা বা ধর্মঠাকুরের মাইক্রো-পরিসর। লক্ষণীয় যে প্রাকঔপনিবেশিক কালখন্ডে এই সমস্ত মাইক্রো-পরিসরগুলো ছিল গুরুত্বপূর্ণ, তার রচয়িতারা নন। তার কারণ সৃজনশীলতার ক্ষেত্রে ব্যক্তিমালিকানার উদ্ভব ও বিকাশ ইউরোপীয় অধিবিদ্যাগত মননবিশ্বের ফসল। সাম্রাজ্যবাদীরা প্রতিটি উপনিবেশে গিয়ে এই ফসলটির চাষ করেছে।
ইতিহাসের দর্শন নিয়ে কাজ করার সময়ে আমার মনে হয়েছিল যে স্পেস বা স্থানিকতার অবদান হল পৃথিবী জুড়ে হাজার রকমের ভাষার মানুষ, হাজার রকমের উচ্চারণ ও বাকশৈলী, যখন কিনা ভাষা তৈরির ব্যাপারে মানুষ জৈবিকভাবে প্রোগ্রামড। একদিকে এই বিস্ময়কর বহুত্ব; অন্যদিকে, সময়কে একটি মাত্র রেখা-বরাবর এগিয়ে যাবার ভাবকল্পনাটি, যিনি ভাবছেন সেই ব্যক্তির নির্বাচিত ইচ্ছানুযায়ী, বহু ঘটনাকে, যা অন্যত্র ঘটে গেছে বা ঘটছে, তাকে বেমালুম বাদ দেবার অনুমিত নকশা গড়ে ফ্যালে। বাদ দেবার এই ব্যাপারটা, আমি সেসময়ে যতটুকু বুঝেছিলুম, স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল লর্ড কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বাঙালির ডিসকোসটি উচ্চবর্গের নিয়ন্ত্রণে চলে যাওয়ায়, যার ফলে নিম্নবর্গের যে প্রাকঔপনিবেশিক ডিসকোর্স বাঙালি সংস্কৃতিতে ছেয়ে ছিল, তা ঔপনিবেশিক আমলে লোপাট হয়ে যাওয়ায়। আমার মনে হয়েছিল যে ম্যাকলে সাহেবের চাপানো শিক্ষাপদ্ধতির কারণে বাঙালির নিজস্ব স্পেস বা পরিসরকে অবজ্ঞা করে ওই সময়ের অধিকাংশ কবি লেখক মানসিকভাবে নিজেদের শামিল করে নিয়েছিলেন ইউরোপীয় সময়রেখাটিতে। একারণেই, তখনকার প্রাতিষ্ঠানিক সন্দর্ভের সঙ্গে হাংরি আন্দোলনের প্রতিসন্দর্ভের সংঘাত আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল প্রথম বুলেটিন থেকেই এবং তার মাত্রা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছিল প্রতিটি বুলেটিন প্রকাশিত হবার সাথে-সাথে, যা আমি বহু পরে জানতে পারি, ‘কাউন্সিল ফর কালচারাল ফ্রিডাম’-এর সচিব এ.বি.শাহ, ‘পি.ই.এন ইনডিয়ার অধ্যক্ষ নিসিম এজেকিয়েল, এবং ভারত সরকারের সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা পুপুল জয়াকরের কাছ থেকে।
আমনধারা সংঘাত বঙ্গজীবনে ইতোপূর্বে ঘটেছিল। ইংরেজরা সময়কেন্দ্রিক মননবৃত্তি আনার পর প্রাগাধুনিক পরিসরমূলক বা স্থানিক ভাবনা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য বাঙালি ভাবুকের জীবনে ও তার পাঠবস্তুতে প্রচন্ড ঝাঁকুনি আর ছটফটানি, রচনার আদল-আদরায় পরিবর্তনসহ, দেখা দিয়েছিল, যেমন ইয়ং বেঙ্গল সদস্যদের ক্ষেত্রে (হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিরী, রাধানাথ শিকদার, প্যারীচাঁদ মিত্র, শিবচন্দ্র দেব ও দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়) এবং মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও আরও অনেকের ক্ষেত্রে। একইভাবে, হাংরি আন্দোলন যখন সময় কেন্দ্রিক ঔপনিবেশিক চিন্তাতন্ত্র থেকে ছিড়ে আলাদা হয়, উত্তর ঔপনিবেশিক আমলে আবার স্থানিকতার চিন্তাতন্ত্রে ফিরে যাবার চেষ্টা করেছিল, তখন আন্দোলনকারীদের জীবনে, কার্যকলাপে ও পাঠবস্তুর আদল-আদরায় অনুরূপ ঝাঁকুনি, ছটফটানি ও সমসাময়িক নন্দন কাঠামো থেকে নিস্কৃতির প্রয়াস দেখা গিয়েছিল। তা নাহলে আর হাংরি আন্দোলনকারীরা সাহিত্য ছাড়াও রাজনীতি, ধর্ম, উদ্দেশ্য, স্বাধীনতা, দর্শনভাবনা, ছবি আঁকা, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ে ইস্তাহার প্রকাশ করবেন কেন।
হাংরি আন্দোলনের সময়কাল খুব সংক্ষিপ্ত, ১৯৬১ থেকে ১৯৬৫ পর্যন্ত। এই ছোট্ট সময়ে শতাধিক ছাপান আর সাইক্লোস্টাইল করা বুলেটিন প্রকাশ করা হয়েছিল, অধিকাংশই হ্যান্ডবিলের মতন ফালিকাগজে, কয়েকটা দেয়াল-পোস্টারে, তিনটি একফর্মার মাপে, এবং একটি (যাতে উৎপলকুমার বসুর ‘পোপের সমাধি’ শিরোনামের বিখ্যাত কবিতাটি ছিল) কুষ্ঠিঠিকুজির মতন দীর্ঘ কাগজে। এই যে হ্যান্ডবিলের আকারে সাহিত্যকৃতি প্রকাশ, এরও পেছনে ছিল সময়কেন্দ্রিক ভাবধারাকে চ্যালেঞ্জের প্রকল্প। ইউরোপীয় সাহিত্যিকদের পাঠবস্তুতে তো বটেই, মাইকেল মধুসুদন দত্তর প্রজন্ম থেকে বাংলা সন্দর্ভে প্রবেশ করেছিল শিল্প-সাহিত্যের নশ্বরতা নিয়ে হাহাকার। পরে, কবিতা পত্রিকা সমগ্র, কৃত্তিবাস পত্রিকা সমগ্র, শতভিষা পত্রিকা সমগ্র ইত্যাদি দুই শক্ত মলাটে প্রকাশের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা দেয়া হয়েছে সাম্রাজ্যবাদী ইউরোপের এই নন্দনতাত্ত্বিক হাহাকারটিকে। পক্ষান্তরে, ফালিকাগজে প্রকাশিত রচনাগুলো দিলদরাজ বিলি করে দেয়া হতো, যে প্রক্রিয়াটি হাংরি আন্দোলনকে দিয়েছিল প্রাকঔপনিবেশিক সনাতন ভারতীয় নশ্বরতাবোধের গর্ব। সেই সব ফালিকাগজ, যারা আন্দোলনটি আরম্ভ করেছিলেন, তাঁরা কেউই সংরক্ষণ করার বোধ দ্বারা তাড়িত ছিলেন না, এবং কারোর কাছেই সবকটি পাওয়া যাবে না। ইউরোপীয় সাহিত্যে নশ্বরতাবোধের হাহাকারের কারণ হল ব্যক্তিমানুষের ট্র্যাজেডিকে কেন্দ্রীয় ভূমিকা প্রদান। যে ট্র্যাজেডি-ভাবনা গ্রেকো-রোমান ব্যক্তি এককের পতনযন্ত্রণাকে মহৎ করে তুলেছিল পরবর্তীকালের ইউরোপে তা বাইবেলোক্ত প্রথম মানুষের ‘অরিজিনাল সিন’ তত্ত্বের আশ্রয়ে নশ্বরতাবোধ সম্পর্কিত হাহাকারকে এমন গুরুত্ব দিয়েছিল যে এলেজি এবং এপিটাফ লেখাটি সাহিত্যিক জীবনে যেন অত্যাবশক ছিল।
আমরা পরিকল্পনা করেছিলুম যে সম্পাদনা ও বিতরণের কাজ দেবী রায় করবেন, নেতৃত্ব দেবেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সংগঠিত করার দিকটা দেখবেন দাদা সমীর রায়চৌধুরী, আর ছাপা এবং ছাপানোর খরচের ভার আমি নেব। প্রথমেই অসুবিধা দেখা দিল। পাটনায় বাংলা ছাপাবার প্রেস পাওয়া গেল না। ফলে ১৯৬১ সালের নভেম্বরে যে বুলেটিন প্রকাশিত হল, তা ইংরেজিতে। এই কবিতার ইশতাহারে আগের প্রজন্মের চারজন কবির নাম থাকায় শক্তি চট্টোপাধ্যায় ক্ষুন্ন হয়েছিলেন বলে ডিসেম্বরে শেষ প্যারা পরিবর্তন করে পুনঃপ্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৬৩ সালের শেষ দিকে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে অংশগ্রহণকারীদের নামসহ এই ইশতাহারটি আরেকবার বেরোয়। ১৯৬২ সালের শেষাশেষি সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটতে থাকে। দাদার বন্ধু উৎপলকুমার বসু, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় যোগ দেন। আমার বন্ধু সুবিমল বসাক, অনিল করঞ্জাই, করুণানিধান মুখোপাধ্যায় যোগদেন। সুবিমল বসাকের বন্ধু প্রদীপ চৌধুরী, সুবো আচার্য, অরূপরতন বসু, বাসুদেব দাশগুপ্ত সুভাষ ঘোষ, সতীন্দ্র ভৌমিক, হরনাথ ঘোষ, নীহার গুহ, শৈলেশ্বর ঘোষ, অশোক চট্টোপাধ্যায়, অমৃততনয় গুপ্ত, ভানু চট্টোপাধ্যায়, শংকর সেন, যোগেশ পান্ডা, মনোহার দাশ যোগ দেন। তখনকার দিনে বামপন্থী ভাবধারার বুদ্ধিজীবীদের ওপর পুলিশ নজর রাখত। দেবী রায় লক্ষ্য করেন নি যে পুলিশের দুজন ইনফর্মার হাংরি আন্দোলনকারীদের যাবতীয় বই পত্র, বুলেটিন ইত্যাদি সংগ্রহ করে লালবাজারের প্রেস সেকশানে জমা দিচ্ছে এবং সেখানে ঢাউস সব ফাইল খুলে ফেলা হয়েছে।
এতজনের লেখালিখি থেকে সেই সময়কার প্রধান সাহিত্যিক সন্দর্ভের তুলনায় হাংরি আন্দোলন যে প্রদিসন্দর্ভ গড়ে তুলতে চাইছিল, সে রদবদল ছিল দার্শনিক এলাকার, বৈসাদৃশ্যটা ডিসকোর্সের, পালাবদলটা ডিসকার্সিভ প্র্যাকটিসের, বৈভিন্ন্যটা কখন-ভাঁড়ারের, পার্থক্যটা উপলব্ধির স্তরায়নের, তফাতটা প্রস্বরের, তারতম্যটা কৃতি-উৎসের। তখনকার প্রধান মার্কেট-ফ্রেন্ডলি ডিসকোর্সটি ব্যবহৃত হতো কবিলেখকের ব্যক্তিগত তহবিল সমৃদ্ধির উদ্দেশ্যে। হাংরি আন্দোলনকারীরা সমৃদ্ধ করতে চাইলেন ভাষার তহবিল, বাচনের তহবিল, বাকবিকল্পের তহবিল, অন্ত্যজ শব্দের তহবিল, শব্দার্থের তহবিল, নিম্নবর্গীয় বুলির তহবিল, সীমালঙ্ঘনের তহবিল, অধ:স্তরীয় রাগবৈশিষ্ট্যের তহবিল, স্পৃষ্টধ্বনির তহবিল, ভাষিক ইরর্যাশনালিটির তহবিল, শব্দোদ্ভটতার তহবিল, প্রভাষার তহবিল, ভাষিক ভারসাম্যহীনতার তহবিল, রূপধ্বনির প্রকরণের তহবিল, বিপর্যাস সংবর্তনের তহবিল, স্বরন্যাসের তহবিল, পংক্তির গতিচাঞ্চল্যের তহবিল, সন্নিধির তহবিল, পরোক্ষ উক্তির তহবিল, স্বরণ্যাসের তহবিল, পাঠবস্তুর অন্তঃস্ফোটিক্রিয়ার তহবিল, তড়িত বাঞ্জনার তহবিল, অপস্বর-উপস্বরের তহবিল, সাংস্কৃতিক সন্নিহিতির তহবিল, বাক্যের অধোগঠনের তহবিল, খন্ডবাক্যের তহবিল, বাক্যনোঙরের তহবিল, শীংকৃত ধ্বনির তহবিল, সংহিতাবদলের তহবিল, যুক্তিছেদের তহবিল, আপতিক ছবির তহবিল, সামঞ্জস্যভঙ্গের তহবিল, কাইনেটিক রূপকল্পের তহবিল ইত্যাদি।
ইতোপূর্বে ইযংবেঙ্গলের সাংস্কৃতিক উথাল-পাথাল ঘটে থাকলেও, বাংলা শিল্প সাহিত্যে আগাম ঘোষণা করে, ইশতাহার প্রকাশ করে, কোন আন্দোলন হয়নি। সাহিত্য এবং ছবি আঁকাকে একই ভাবনা-ফ্রেমে আনার প্রয়াস, পারিবারিক স্তরে হয়ে থাকলেও, সংঘবদ্ধ গোষ্ঠীর মাধ্যমে হয়নি। ফলত দর্পণ, জনতা, জলসা ইত্যাদি পত্রিকায় আমাদের সম্পর্কে বানানো খবর পরিবেশিত হওয়া আরম্ভ হল। হাংরি আন্দোলনের রাজনৈতিক ইশতাহার নিয়ে প্রধান সম্পাদকীয় বেরোল যুগান্তর দৈনিকে। আমার আর দেবী রায়ের কার্টুন প্রকাশিত হল দি স্টেটসম্যান পত্রিকায়। হেডলাইন হল ব্রিৎস পত্রিকায়। সুবিমল বসারের প্রভাবে হিন্দি ভাষায় রাজকমল চৌধুরী আর নেপালি ভাষায় পারিজাত হাংরি আন্দোলনের প্রসার ঘটালেন। আসামে ছড়িয়ে পড়ল পাঁক ঘেটে পাতালে পত্রিকাগোষ্ঠীর সদস্যদের মাঝে। ছড়িয়ে পড়ল বগুড়ার বিপ্রতীক এবং ঢাকার স্বাক্ষর ও কণ্ঠস্বর পত্রিকাগুলোর সদস্যদের মাঝে, এবং মহারাষ্ট্রের অসো পত্রিকার সদস্যদের ভেতর। ঢাকার হাংরি আন্দোলনকারীরা (বুলবুল খান মাহবুব, অশোক সৈয়দ, আসাদ চৌধুরী, শহিদুর রহমান, প্রশান্ত ঘোষাল, মুস্তফা আনোয়ার প্রমুখ) জানতেন না যে আমি কেন প্রথম হাংরি বুলেটিনগুলো ইংরেজিতে প্রকাশ করেছিলুম। ফলে তাঁরাও আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন ইংরেজিতে ইশতাহার প্রকাশের মাধ্যমে।
যার-যেমন-ইচ্ছে লেখালেখির স্বাধীনতার দরুন হাংরি আন্দোলনকারীদের পাঠবস্তুতে যে অবাধ ডিক্যাননাইজেশান, আঙ্গিকমুক্তি, যুক্তিভঙ্গ, ডিন্যারেটিভাইজেশান, অনির্ণেয়তা, মুক্ত সমাপ্তি ইত্যাদির সূত্রপাত ঘটে, সেগুলোর যথার্থ সার্থকতা ও প্রাসঙ্গিকতার প্রশ্ন উত্থাপন করতে থাকেন তখনকার বিদ্যায়তনিক আলোচকরা, যাঁরা বিবিধতাকে মনে করেছিলেন বিশৃঙ্খলা, সমরূপ হবার অস্বীকৃতিকে মনে করেছিলেন অন্তর্ঘাত, সন্দেহপ্রবণতাকে মনে করেছিলেন অক্ষমতা, ঔপনিবেশিক চিন্তনতন্ত্রের বিরোধীতাকে মনে করেছিলেন অসামাজিক, ক্ষমতাপ্রতাপের প্রতিরোধকে মনে করেছিলেন সত্যের খেলাপ। তাঁদের ভাবনায় মতবিরোধিতা মানেই যেন অসত্য, প্রতিবাদের যন্ত্রানুষঙ্গ যেন সাহিত্যসম্পর্কহীন। মতবিরোধিতা যেহেতু ক্ষমতার বিরোধিতা, তাই তাঁরা তার যে কোন আদল ও আদরাকে হেয় বলে মনে করেছিলেন, কেননা প্রতিবিম্বিত ভাবকল্পে মতবিরোধীতা অনিশ্চয়তার প্রসার ঘটায়, বিশৃঙ্খলার সূত্রপাত করে বলে অনুমান করে নেয়া হয়, তা যদি সাহিত্যকৃতি হয় তাহলে সাহিত্যিক মননবিশ্বে, যদি রাজনৈতিক কর্মকান্ড হয় তাহলে রাষ্ট্রের অবয়বে। এখানে বলা দরকার যে, পশ্চিমবাংলায় তখনও রাজনৈতিক পালাবদল ঘটেনি। তখনকার প্রতিবিম্বিত বিদ্যায়তনিক ভাবাদর্শে, অতএব, যারা মতবিরোধের দ্বারা অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করছিল, অর্থাৎ হাংরি আন্দোলনকারীরা, তারা অন্যরকম, তারা অপর, তারা প্রান্তিক, তারা অনৈতিক, তারা অজ্ঞান, তারা সত্যের মালিকানার অযোগ্য। বলাবাহুল্য যে, ক্ষমতা ও সত্যের অমনতর পার্থক্যহীন পরিসরে যাদের হাতে ক্ষমতা তাদের কব্জায় সত্যের প্রভূত্ব। অজ্ঞানের চিন্তাভাবনাকে মেরামত করার দায়, ওই তর্কে, সুতরাং, সত্য মালিকের।
প্রাগুক্ত মেরামতির কাজে নেমে বিদ্যায়তনিক আলোচকরা হাংরি আন্দোলনের তুলনা করতে চাইছিলেন পাঁচের দশকে ঘটে যাওয়া দুটি পাশ্চাত্য আন্দোলনের সঙ্গে। ব্রিটেনের অ্যাংরি ইয়াং ম্যান ও আমেরিকার বিট জেনারেশনের সঙ্গে। তিনটি বিভিন্ন দেশের ঘটনাকে তাঁরা এমনভাবে উল্লেখ ও উপস্থাপন করতেন, যেন এই তিনটি একই প্রকার সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি, এবং তিনটি দেশের আর্থ-রাজনৈতিক কাঠামো, কৌমসমাজের ক্ষমতা-নকশা, তথা ব্যক্তিপ্রতিস্ব নির্মিতির উপাদানগুলো অভিন্ন। আমার মনে হয় বিদ্যায়তনিক ভাবনার প্রধান অন্তরায় হিসেবে কাজ করেছে সীমিত ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞতা, অর্থাৎ কেবলমাত্র বাংলা ভাষাসাহিত্য বিষয়ক পঠন-পাঠন। যার দরুণ সমাজ ও ব্যক্তিমানুষের জীবনকে তাঁরা ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন সাহিত্যের উপকরণ প্রয়োগ করে। যে-সমস্ত উপাদানের সাহায্যে কৌমসমাজটি তার ব্যক্তি এককদের প্রতিস্ব নির্মাণ করে, সেগুলো ভেবে দেখার ও বিশ্লেষণের প্রয়াস তাঁরা করতেন না। প্রতিস্ব-বিশেষের পাঠবস্তু কেন অমন চেহারায় গোচরে আসছে, টেক্সট-বিশেষের প্রদায়ক গুণনীয়ক কী-কী, পুঁজিপ্রতাপের কৌমকৃৎকৌশল যে প্রতিস্ব-পীড়ন ঘটাচ্ছে তার পাপে পাঠবস্ত-গঠনে মনস্তাত্ত্বিক ও ভাষানকশা কীভাবে ও কেন পাল্টাচ্ছে, আর তাদের আখ্যান ঝোঁকের ফলশ্রুতিই বা কেন অমনধারা, এগুলো নিয়ে চিন্তাভাবনা করার বদলে, তাঁরা নিজেদের ব্যক্তিগত ভালোলাগা (ফিল গুড) নামক সাবজেকটিভ খপ্পরে পড়ে পাঠক-সাধারণকে সেই ফাঁদে টানতে চাইতেন। যে কোনও পাঠবস্ত একটি স্থানিক কৌমসমাজের নিজস্ব ফসল। কৌমনিরপেক্ষ পাঠবস্ত অসম্ভব।
কেবল উপরোক্ত দুটি পাশ্চাত্য সাহিত্যিক ঘটনা নয়, ষাটের দশকের বাংলা সাহিত্যে অন্যান্য যে আন্দোলনগুলো ঘটেছিল, যেমন নিমসাহিত্য, শ্রুতি, শাস্ত্রবিরোধী এবং ধ্বংসকালীন, তাদের সঙ্গেও হাংরি আন্দোলনের জ্ঞান-পরিমন্ডল, দর্শন-পরিসর, প্রতিপ্রশ্ন-প্রক্রিয়া, অভিজ্ঞতা-বিন্যাস, চিন্তার-আকরণ, প্রতীতি, বিশ্লেষণী আকল্প, প্রতিবেদনের সীমান্ত, প্রকল্পনার মনোবীজ, বয়ন-পরাবয়ন, ভাষা-পরাভাষা, জগৎ-পরাজগৎ, বাচনিক নির্মিতি, সত্তাজিজ্ঞাসা, উপস্থাপনার ব্যঞ্জনা, অপরত্ববোধ, চিহ্নাদির অন্তর্বয়ন, মানবিক সম্পর্ক বিন্যাসের অনুষঙ্গ, অভিধাবলীর তাৎপর্য, উপলব্ধির উপকরণ, স্বভাবাতিযায়ীতা, প্রতিস্পর্ধা, কৌমসমাজের অর্গল, গোষ্ঠীক্রিয়ার অর্থবহতা, প্রতাপবিরোধী অবস্থানের মাত্রা, প্রতিদিনের বাস্তব, প্রান্তিকায়নের স্বাতন্ত্র্য, বিকল্প অবলম্বন সন্ধান, চিহ্নায়নের অন্তর্ঘাত, লেখন-গ্রন্থনা, দেশজ অধিবাস্তব, অভিজ্ঞতার সূত্রায়ন-প্রকরণ, প্রেক্ষাবিন্দুর সমন্বয়, সমষ্টী পীড়াপুঞ্জ ইত্যাদি ব্যাপারে গভীর ও অসেতুসম্ভব পার্থক্য ছিল। ষাটের দশকের ওই চারটি আন্দোলনের সঙ্গে হাংরি প্রতিসন্দর্ভের যে-মিল ছিল তা হল এই যে পাঁচটি আন্দোলনই লেখকপ্রতিম্ব থেকে রোশনাইকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল পাঠবস্তর ওপর। অর্থাৎ লেখকের কেরামতি বিচার্য নয়, যা বিচার্য তা হল পাঠবস্তুর খুঁটিনাটি। লেখকের বদলে পাঠবস্তু যে গুরুত্বপূর্ণ, এই সনাতন ভারতীয়তা, মহাভারত ও রামায়ণ পাঠবস্তু দুটির দ্বারা প্রমাণিত।
অনুশাসন মুক্তির ফলে, লিটল ম্যাগাজিনের নামকরণের ক্ষেত্রে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে এসেছিল হাংরি আন্দোলন, যে, তারপর থেকে পত্রিকার নাম রাখার ঐতিহ্য একবারে বদলে গেল। কবিতা, ধ্রুপদী, কৃত্তিবাস, শতভিষা, উত্তরসূরী, অগ্রণী ইত্যাদি থেকে একশ আশি ডিগ্রি ঘুরে গিয়ে হাংরি আন্দালনকারীরা তাঁদের পত্রিকার নাম রাখলেন জেব্রা, উন্মার্গ, ওয়েস্টপেপার, ফুঃ কনসেনট্রেশন ক্যাম্প ইত্যাদি। অবশ্য সাহিত্য শিল্পকে উন্মার্গ আখ্যাটি জীবনানন্দ দাশ বহু পূর্বে দিয়ে গিয়েছিলেন, যদিও হাংরি আন্দালনের সময় পর্যন্ত তিনি তেমন প্রতিষ্ঠা পান নি। জেব্রা নামকরণটি ছিল পাঠকের জন্যে নিশ্চিন্তে রাস্তা পার হয়ে হাংরি পাঠবস্তুর দিকে এগোবার ইশারা। হাংরি আন্দোলন সংঘটিত হবার আগে ওই পত্রিকাগুলোর নামকরণেই কেবল এলিটিজম ছিল তা নয়, সেসব পত্রিকাগুলোর একটি সম্পাদকীয় বৈশিষ্ট্য ছিল। বুর্জোয়া মূল্যবোধ প্রয়োগ করে একে-তাকে বাদ দেয়া বা ছাঁটাই করা, যে কারণে নিম্নবর্ণের লেখকের পাঠবস্ত সেগুলোর পৃষ্ঠায় অনুপস্থিত, বিশেষ করে কবিতা। আসলে কোন-কোন রচনাকে ‘টাইমলেস’ বলা হবে সে জ্ঞানটুকু ওই মূল্যবোধের ধারক-বাহকরা মনে করতেন তাঁদের কুক্ষিগত, কেননা সময় তো তাঁদের চোখে একরৈখিক, যার একেবারে আগায় আছেন কেবল তাঁরা নিজে।
‘টাইমলেস’ কাজের উদ্বেগ থেকে পয়দা হয়েছিল ‘আর্ট ফর আর্টস সেক’ ভাবকল্পটি, যা উপনিবেশগুলোয় চারিয়ে দিয়ে মোক্ষম চাল দিয়েছিল সাম্রাজ্যবাদী ইউরোপ। এই ভাবকল্পটির দ্বারা কালো, বাদামি, হলদে চামড়ার মানুষদের বহুকাল পর্যন্ত এমন সম্মোহিত করে রেখেছিল সাম্রাজ্যবাদী নন্দনভাবনা যাতে সাহিত্য-শিল্প হয়ে যায় উদ্দেশ্যহীন ও সমাজমুক্ত, যাতে পাঠবস্তু হয়ে যায় বার্তাবর্জিত, যাতে সন্দর্ভের শাসক-বিরোধী অন্তর্ঘাতী ক্ষমতা লুপ্ত হয়, এবং তা হয়ে যায় জনসংযোগহীন। হাংরি বুলেটিন যেহেতু প্রকাশিত হতো হ্যান্ডবিলের মতন ফালিকাগজে, তা পরের দিনই সময় থেকে হারিয়ে যেত। নব্বইটির বেশি বুলেটিন চিরকালের জন্যে হারিয়ে গেছে। লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরির পক্ষেও ও বুলেটিনগুলো সংগ্রহ ও সংরক্ষণ সম্ভব হয়নি।
যে কোন আন্দোলনের জন্ম হয় কোন না কোন আধিপত্য প্রণালীর বিরুদ্ধে। তা সে রাজনৈতিক আধিপত্য হোক বা সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আর্থিক, নৈতিক, নান্দনিক, ধার্মিক, সাহিত্যিক, শৈল্পিক ইত্যাদি আধিপত্য হোক না কেন। আন্দোলন-বিশেষের উদ্দেশ্য, অভিমুখ, উচ্চাকাঙ্খা, গন্তব্য হল সেই প্রণালীবদ্ধতাকে ভেঙে ফেলে পরিসরটিকে মুক্ত করা। হাংরি আন্দোলন কাউকে বাদ দেবার প্রকল্প ছিল না। যে কোন কবি বা লেখক, ওই আন্দোলনের সময়ে যিনি নিজেকে হাংরি আন্দোলনকারী মনে করেছেন, তাঁর খুল্লমখুল্লা স্বাধীনতা ছিল হাংরি বুলেটিন বের করার। বুলেটিনগুলোর প্রকাশকদের নাম-ঠিকানা দেখলেই স্পষ্ট হবে (অন্তত যে-কটির খোঁজ মিলেছে তাদের ক্ষেত্রেও) যে, তা ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিভিন্নজন কর্তৃক ১৯৬৩-র শেষ দিকে এবং ১৯৬৪-র প্রথমদিকে প্রকাশিত। ছাপার খরচ অবশ্য আমি বা দাদা যোগাতাম, কেননা, অধিকাংশ আন্দোলনকারীর আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না। শক্তি চট্টোপাধ্যায়, বিনয় মজুমদার, উৎপল কুমার বসুও নিজের খরচে প্রকাশ করেছিলেন বুলেটিন। অর্থাৎ হাংরি বুলেটিন কারোর প্রায়ভেট প্রপার্টি ছিল না। এই বোধের মধ্যে ছিল পূর্বতন সন্দর্ভগুলোর মনোবীজে লুকিয়ে থাকা সত্ত্বাধিকার বোধকে ভেঙে ফেলার প্রতর্ক যা সাম্রাজ্যবাদী ইউরোপীয়রা এদেশে এনেছিল। ইউরোপীয়রা আসার আগে বঙ্গদেশে পার্সোনাল পজেশান ছিল, কিন্তু প্রায়ভেট প্রপার্টি ছিল না।
হাংরি আন্দোলনের কোন হেড কোয়ার্টার, হাইকমান্ড, গভর্নিং কাউনসিল বা সম্পাদকের দপ্তর ধরণের ক্ষমতাকেন্দ্র ছিল না, যেমন ছিল কবিতা, ধ্রুপদী, কৃত্তিবাস ইত্যাদি পত্রিকার ক্ষেত্রে, যার সম্পাদক বাড়ি বদল করলে পত্রিকা দপ্তরটি নতুন বাড়িতে উঠে যেত। হাংরি আন্দোলন কুক্ষিগত ক্ষমতাকেন্দ্রের ধারণাকে অতিক্রম করে প্রতিসন্দর্ভকে ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিল প্রান্তবর্তী এলাকায়, যে কারণে কেবল বহির্বঙ্গের বাঙালি শিল্পী-সাহিত্যিক ছাড়াও তা হিন্দি, উর্দু, নেপলি, অসমীয়া, মারাঠি ইত্যাদি ভাষায় ছাপ ফেলতে পেরেছিল। এখনও মাঝে মধ্যে কিশোর-তরুণরা এখান-সেখান থেকে নিজেদের হাংরি আন্দোলনকারী ঘোষণা করে গর্বিত হন, যখন কিনা আন্দোলনটি চল্লিশ বছর আগে, ১৯৬৫ সালে ফুরিয়ে গিয়েছে।
বিয়াল্লিশ বছর আগে সুবিমল বসাক, হিন্দি কবি রাজকমল চৌধুরীর সঙ্গে, একটি সাইক্লোস্টাইল করা ত্রিভাষিক (বাংলা-হিন্দি-ইংরেজি) হাংরি বুলেটিন প্রকাশ করেছিলেন, তদানীন্তন সাহিত্যিক সন্দর্ভের প্রেক্ষিতে হাংরি প্রতিসন্দর্ভ যে কাজ উপস্থাপন করতে চাইছে তা স্পষ্ট করার জন্যে। তাতে দেয়া তালিকাটি থেকে আন্দোলনের অভিমুখের কিছুটা হদিশ মিলবে:
১৯৬৩ সালের শেষ দিকে সুবিমল বসাকের আঁকা বেশ কিছু লাইন ড্রইং, যেগুলো ঘন-ঘন হাংরি বুলেটিনে প্রকাশিত হচ্ছিল, তার দরুণ তাঁকে পরপর দুবার কফিহাউসের সামনে ঘিরে ধরলেন অগ্রজ বিদ্বজ্জন এবং প্রহারে উদ্যত হলেন, এই অজুহাতে যে সেগুলো অশ্লীল। একই অজুহাতে কফিহাউসের দেয়ালে সাঁটা অনিল করঞ্জাইয়ের আঁকা পোস্টার আমরা যতবার লাগালুম ততবার ছিঁড়ে ফেলে দেয়া হল। বোঝা যাচ্ছিল যে, কলোনিয়াল ইসথেটিক রেজিমের চাপ তখনও অপ্রতিরোধ্য। হাংরি আন্দোলনের ১৫ নম্বর বুলেটিন এবং ৬৫ নং বুলেটিন, যথাক্রমে রাজনৈতিক ও ধর্ম সম্পর্কিত ইশতাহারের, যাকে বলে স্লো বলিং এফেক্ট, আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল, এবং আমাদের অজ্ঞাতসারে ক্রুদ্ধ করে তুলছিল মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেনের এসট্যাবলিশমেন্টকে। আজকের ভারতবর্ষের দিকে তাকিয়ে ইশতাহার দুটিকে অলমোস্ট প্রফেটিক বলা যায়। এরপর, যখন রাক্ষস জোকার মিকিমাউস জন্তজানোয়ার ইত্যাদির কাগুজে মুখোশে ‘দয়া করে মুখোশ খুলে ফেলুন’ বার্তাটি ছাপিয়ে হাংরি আন্দোলনের পক্ষ থেকে মুখ্য ও অন্যান্য মন্ত্রীদের মুখ্য ও অন্যান্য সচিবদের জেলা শাসকদের, সংবাদপত্র মালিক ও সম্পাদকদের, বাণিজ্যিক লেখকদের পাঠান হল, তখন সমাজের এলিট অধিপতিরা আসরে নামলেন। এ ব্যাপারে কলকাঠি নাড়লেন একটি পত্রিকা গোষ্ঠীর মালিক, তাঁর বাংলা দৈনিকের বার্তা সম্পাদক এবং মার্কিন গোয়েন্দা বিভাগের খোরপোষে প্রতিপালিত একটি ইংরেজি ত্রৈমাসিকের কর্তাব্যক্তিরা।
১৯৬৪ এর সেপ্টেম্বরে রাষ্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে গ্রেপ্তার হলুম আমি, প্রদীপ চৌধুরী, সুভাষ ঘোষ, দেবী রায়, শৈলেশ্বর ঘোষ এবং দাদা সমীর রায়চৌধুরী। এই অভিযোগে উৎপল কুমার বসু, সুবিমল বসাক, বাসুদেব দাশগুপ্ত, সুবো আচার্য এবং রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট ইসু হয়ে থাকলেও, তাঁদের প্রেপ্তার করা হয়নি। এরকম একটি অভিযোগ এই জন্যে চাপান হয়েছিল যাতে বাড়ি থেকে থানায় এবং থানা থেকে আদালতে হাতে হাতকড়া পরিয়ে আর কোমরে দড়ি বেঁধে চোরডাকাতদের সঙ্গে সবায়ের সামনে দিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। অন্তর্ঘাতের অভিযোগটি সেপ্টেম্বর ১৯৬৪ থেকে মে ১৯৬৫ পর্যন্ত বজায় ছিল, এবং ওই নয় মাস যাবৎ রাষ্ট্রযন্ত্রটি তার বিভিন্ন বিভাগের মাধ্যমে হাংরি আন্দোলনকারীরূপে চিহ্নিত প্রত্যেকের সম্পর্কে খুটিনাটি তথ্য সংগ্রহ করে ফেলেছিল, এবং তাদের তখন পর্যন্ত যাবতীয় লেখালেখি সংগ্রহ করে ঢাউস-ঢাউস ফাইল তৈরি করেছিল, যেগুলো লালবাজারে পুলিশ কমিশনারের কনফারেন্স রুমের টেবিলে দেখেছিলুম, যখন কলকাতা পুলিশ, স্বরাষ্ট্র দফতর, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগ ও ভারতীয় সেনার উচ্চপদস্থ আধিকারিক এবং পশ্চিমবঙ্গের অ্যাডভোকেট জেনারালকে নিয়ে গঠিত একটি বোর্ড আমাকে আর দাদা সমীর রায়চৌধুরীকে কয়েক ঘন্টা জেরা করেছিল।
অভিযোগটি কোন সাংস্কৃতিক অধিপতির মস্তিস্কপ্রসূত ছিল জানি না। তবে অ্যাডভোকেট জেনারেল মতামত দিলেন যে এরকম আজেবাজে তথ্যের ওপর তৈরি এমন সিরিয়াস অভিযোগ দেখলে আদালত চটে যাবে। তখনকার দিনে টাডা-পোটা ধরণের আইন ছিল না। ফলত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুলে নিয়ে ১৯৬৫ সালের মে মাসে বাদবাকি সবাইকে ছেড়ে দিয়ে কেবল আমার বিরুদ্ধে মামলা রুজু হল, এই অভিযোগে যে সাম্প্রতিকতম হাংরি বুলেটিনে প্রকাশিত আমার ‘প্রচন্ড বৈদ্যুতিক ছুতার’ কবিতাটি অশ্লীল। আমার বিরুদ্ধে মামলাটা দায়ের করা সম্ভব হল শৈলেশ্বর ঘোষ এবং সুভাষ ঘোষ আমার বিরুদ্ধে রাজসাক্ষী হয়ে গেলেন বলে। অর্থাৎ হাংরি আন্দোলন ফুরিয়ে গেল। ওনারা দুজনে হাংরি আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে মুচলেকা দিলেন, যার প্রতিলিপি চার্জশিটের সঙ্গে আদালত আমায় দিয়েছিল ।
প্রসিকিউশনের পক্ষে এই দুজন রাজসাক্ষীকে তেমন নির্ভরযোগ্য মনে হয়নি । তাই আমার বিরুদ্ধে সমীর বসু আর পবিত্র বল্লভ নামে দুজন ভুয়ো সাক্ষীকে উইটনেস বক্সে তোলা হয়, যাদের আমি কোন জন্মে দেখিনি, অথচ যারা এমনভাবে সাক্ষ্য দিয়েছিল যেন আমার সঙ্গে কতই না আলাপ-পরিচয়। এই দুজন ভুয়ো সাক্ষীর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আমাকে অপরাধী হিসেবে উপস্থাপন করা। আমার কৌশুলিদের জেরায় এরা দুজন ভুয়ো প্রমাণ হবার সম্ভাবনা দেখা দিলে প্রসিকিউশন আমার বিরুদ্ধে উইটনেস বক্সে তোলে, বলাবাহুল্য গ্রেপ্তারের হুমকি দিয়ে, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, উৎপলকুমার বসু আর সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়কে। ফলে আমিও আমার পক্ষ থেকে সাক্ষী হিসেবে দাঁড় করাই জ্যোতির্ময় দত্ত, তরুণ সান্যাল আর সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে। বহু সাহিত্যিককে অনুরোধ করেছিলুম, কিন্তু এনারা ছাড়া আর কেউ রাজি হননি। শক্তি এবং সুনীল, দুই বন্ধু, একটি মকদ্দমায় পরস্পরের বিরুদ্ধে, চল্লিশ বছর পর ব্যাপারটা অবিশ্বস্য মনে হয়। সবায়ের সাক্ষ্য ছিল বেশ মজাদার, যাকে বলে কোর্টরুম-ড্রামা।
তেরটা আদালতঘরের মধ্যে আমার মকদ্দমাটা ছিল নয় নম্বর এজলাসে। বিচারকের মাথার ওপর হলদে টুনি বালবটা ছাড়া আলোর বালাই ছিল না জানালাহীন ঘরটায়। অবিরাম ক্যাচোর-ক্যাচোর শব্দে অবসর নেবার অনুরোধ জানাত দুই ব্লেডের বিশাল ছাদপাখা। পেশকার গাংগুলি বাবুর অ্যান্টিক টেবিলের লাগোয়া বিচারকের টানা টেবিল, বেশ উঁচু, ঘরের এক থেকে আরেক প্রান্ত, বিচারকের পেছনে দেয়ালে টাঙানো মহাত্মা গান্ধীর ফোকলা-হাসি রঙিন ছবি। ইংরেজরা যাবার পর চুনকাম হয়নি ঘরটা। হয়ত ঘরের ঝুলগুলোও তখনকার। বিচারকের টেবিলের বাইরে, ওনার ডান দিকে, দেয়াল ঘেঁষে, জাল-ঘেরা লোহার শিকের খাঁচা, জামিন-না-পাওয়া বিচারাধীনদের জন্যে, যারা ওই খাঁচার পেছনের দরোজা দিয়ে ঢুকত। খাঁচাটা অত্যন্ত নোংরা। আমি যেহেতু ছিলুম জামিনপ্রাপ্ত, দাঁড়াতুম খাঁচার বাইরে। ঠ্যাঙ ব্যথা করলে, খাঁচায় পিঠ ঠেকিয়ে।
পেশকার মশায়ের টেবিলের কাছাকাছি থাকত গোটাকতক আস্ত-হাতল আর ভাঙা-হাতল চেয়ার, কৌঁসুলিদের জন্যে। ঘরের বাকিটুকুতে ছিল নানা মাপের, আকারের, রঙের নড়বড়ে বেঞ্চ আর চেয়ার, পাবলিকের জন্যে, ছারপোকা আর খুদে আরশোলায় গিজগিজে। টিপেমারা ছারপোকার রক্তে, পানের পিকে, ঘরের দেয়ালময় ক্যালিগ্রাফি। বসার জায়গা ফাঁকা থাকত না। কার মামলা কখন উঠবে ঠিক নেই। ওই সর্বভারতীয় ঘর্মাক্ত গ্যাঞ্জামে, ছারপোকার দৌরাত্মে, বসে থাকতে পারতুম না বলে সারা বাড়ি এদিক-ওদিক ফ্যা-ফ্যা করতুম, এ-এজলাস সে-এজলাস চক্কর মারতুম, কৌতুহলোদ্দীপক সওয়াল-জবাব হলে দাঁড়িয়ে পড়তুম। আমার কেস ওঠার আগে সিনিয়ার উকিলের মুহুরিবাবু আমায় খুঁজে পেতে ডেকে নিয়ে যেতেন। মুহুরিবাবু মেদিনীপুরের লোক, পরতেন হাঁটু পর্যন্ত ধুতি, ক্যাম্বিশের জুতো, ছাইরঙা শার্ট। সে শার্টের ঝুল পেছন দিকে হাঁটু পর্যন্ত আর সামনে দিকে কুঁচকি পর্যন্ত। হাতে লম্বালম্বি ভাঁজ করা ফিকে সবুজ রঙ্গের দশ-বারটা ব্রিফ, যেগুলো নিয়ে একতলা থেকে তিনতলার ঘরে-ঘরে লাগাতার চরকি নাচন দিতেন।
আমার সিনিয়র উকিল ছিলেন ক্রিমিনাল লয়ার চন্ডীচরণ মৈত্র। সাহিত্য সম্পর্কে ওনার কোন রকম ধারণা ছিল না বলে লেবার কোর্টের উকিল সতেন বন্দ্যোপাধ্যায়কেও রাখতে হয়েছিল। চাকরি থেকে সাসপেন্ডেড ছিলুম কেস চলার সময়ে, তার ওপর কলকাতায় আমার মাথা গোঁজার ঠাই ছিল না। খরচ সামলানো অসম্ভব হয়ে গিয়েছিল।
আদালত চত্বরটা সবসময় ভিড়ে গিজগিজ করত। ফেকলু উকিলরা গেটের কাছে দাঁড়িয়ে “সাক্ষী চাই? সাক্ষী চাই? এফিডেফিট হবে।” বলে-বলে চেচাত মক্কেল যোগাড়ের ধান্দায়। সারা বাড়ি জুড়ে যেখানে টুলপেতে টাইপরাইটারে ফটর ফটর ট্যারাবেকা টাইপ করায় সদাব্যস্ত টাইপিস্ট, পাশে চোপসানো মুখ লিটিগ্যান্ট। একতলায় সর্বত্র কাগজ, তেলেভাজা, অমলেট, চা-জলখাবার, ভাতরুটির ঠেক। কোর্ট পেপার কেনার দীর্ঘ কিউ। চাপরাসি- আরদালির কাজে যে সব বিহারিদের আদালতে চাকরি দিয়েছিল ইংরেজরা, তারা চত্বরের খোঁদলগুলো জবরদখল করে সংসার পেতে ফেলেচে। জেল থেকে খতরনাক আসামিরা পুলিশের বন্ধ গাড়িতে এলে, পানাপুকুরে ঢিল পড়ার মতন একটু সময়ের জন্যে সরে যেত ভিড়টা। তারপর যে কে সেই। সন্দর্ভ ও প্রতিসন্দর্ভের সামাজিক সংঘাতক্ষেত্র হিসেবে আদালতের মতন সংস্থা সম্ভবত আর নেই।
সাক্ষ্যাদি শেষ হবার পর দুপক্ষের দীর্ঘ বহস হল একদিন, প্রচুর তর্কাতর্কি হল। আমি খাঁচার কাছে ঠায় দাঁড়িয়ে। রায় দেবার দিন পড়ল ১৯৬৫ সালের আঠাশে ডিসেম্বর। ইতিমধ্যে আমেরিকার ‘টাইম’ ম্যাগাজিনে সংবাদ হয়ে গেছি। যুগান্তর দৈনিকে ‘আর মিছিলের শহর নয়’ এবং ‘যে ক্ষুধা জঠরের নয়’ শিরোনামে প্রধান সম্পাদকীয় লিখলেন কৃষ্ণ ধর। যুগান্তর দৈনিকে সুফী এবং আনন্দবাজার পত্রিকায় চন্ডী লাহিড়ী কার্টুন আঁকলেন আমায় নিয়ে। সমর সেন সম্পাদিত ‘নাউ’ পত্রিকায় পরপর দুবার লেখা হল আমার সমর্থনে। দি স্টেটসম্যান পত্রিকায় হাংরি আন্দোলনের সমর্থনে সমাজ-বিশ্লেষণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হল। ধর্মযুগ, দিনমান, সম্মার্গ, সাপ্তাহিক হিন্দুস্থান, জনসত্তা পত্রিকায় উপর্যুপরি ফোটো ইত্যাদিসহ লিখলেন ধর্মবীর ভারতী, এস. এইচ. বাৎসায়ন অজ্ঞেয়, ফনীশ্বর নাথ রেণু, কমলেশ্বর, শ্রীকান্ত ভর্মা, মুদ্রারাক্ষস, ধুমিল, রমেশ বকশি প্রমুখ। কালিকটের মালায়ালি পত্রিকা যুগপ্রভাত হাংরি আন্দোলনকে সমর্থন করে দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করল। বুয়েনস আয়ার্স-এর প্যানারোমা পত্রিকার সাংবাদিক আমার মকদ্দমা কভার করল। পাটনার দৈনিক দি সার্চলাইট প্রকাশ করল বিশেষ ক্রোড়পত্র। বিশেষ হাংরি আন্দোলন সংখ্যা প্রকাশ করল জার্মানির ক্ল্যাকটোভিডসেডস্টিন পত্রিকা, এবং কুলচুর পত্রিকা ছাপলো সবকটি ইংরেজি ম্যানিফেস্টো। আমেরিকায় হাংরি আন্দোলনকারীদের ফোটো, ছবি-আঁকা, রচনার অনুবাদ ইত্যাদি নিয়ে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করল সল্টেড ফেদার্স, ট্রেস, ইনট্রেপিড, সিটি লাইটস জার্নাল, সান ফ্রানসিসকো আর্থকোয়েক, র্যামপার্টস, ইমেজো হোয়্যার ইত্যাদি লিটল ম্যাগজিন। সম্পাদকীয় প্রকাশিত হল নিউ ইয়র্কের এভারগ্রিন রিভিউ, আর্জেনটিনার এল কর্নো এমপ্লমাদো এবং মেকসিকোর এল রেহিলেতে পত্রিকায়। পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষ করে কলকাতায় টিটকিরি মারা ছাড়া আর কিছু করেন নি বাঙ্গালি সাহিত্যিকরা।
ভুয়ো সাক্ষী, রাজ সাক্ষী আর সরকারি সাক্ষীদের বক্তব্যকে যথার্থ মনে করে আমার পক্ষের সাক্ষীদের বক্তব্য নাকচ করে দিলেন ফৌজদারি আদালতের বিচারক। দুশো টাকা জরিমানা অনাদায়ে এক মাসের কারাদান্ড ধার্য করলে তিনি। আমি হাইকোর্টে রিভিশন পিটিশন করার জন্যে আইনজীবির খোঁজে বেরিয়ে দেখলুম যে খ্যাতিমান কৌঁসুলিদের এক দিনের বহসের ফি প্রায় লক্ষ টাকা, অনেকে প্রতি ঘন্টা হিসেবে চার্জ করেন, তাঁরা ডজনখানেক সহায়ক উকিল দুপাশে দাঁড় করিয়ে বহস করেন। জ্যোতির্ময় দত্ত পরিচয় করিয়ে দিলেন সদ্য লন্ডন-ফেরত ব্যারিস্টার করুণাশঙ্কর রায়ের সঙ্গে। তাঁর সৌজন্যে আমি তখনকার বিখ্যাত আইনজীবি মৃগেন সেনকে পেলুম। নিজের সহায়কদের নিয়ে তিনি কয়েক দিন বসে তর্কের স্ট্রাটেজি কষলেন। ১৯৬৭ সালের ছাব্বিশে জুলাই আমার রিভিশন পিটিশানের শুনানি হল। নিম্ন আদালতের রায় নাকচ করে দিলেন বিচারক টি. পি. মুখার্জি। ফিস ইন্সটলমেন্টে দেবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন করুণাশঙ্কর রায়।
হাংরি আন্দোলন চল্লিশ বছর আগে শেষ হয়ে গেছে। এখন শুরু হয়েছে তাকে নিয়ে ব্যবসা। সমীর চৌধুরী নামে এক ব্যক্তি (আমার দাদার নামের মিলটা কাজে লাগান হয়েছে) ‘হাংরি জেনারেশন রচনা সংকলন’ নামে একটা বই বের করেছেন। তাতে অন্তর্ভূক্ত অধিকাংশ লেখককে আমি চিনি না। শক্তি, সন্দীপন, উৎপল, বিনয়, সমীর, দেবী, সুবিমল, এবং আমার রচনা তাতে নেই। অনিল, করুণা, সুবিমলের আঁকা ছবি নেই। একটিও ম্যানিফেস্টো নেই। বাজার নামক ব্যাপারটি একটি ভয়ংকর সাংস্কৃতিক সন্দর্ভ।
তিন
বাংলা সাহিত্যে হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের প্রভাব নিয়ে অভিজিৎ পাল একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন, এবাদুল হক সম্পাদিত ‘আবার এসেছি ফিরে’ পত্রিকায়, তা থেকে উল্লেখ্য অংশ তুলে দিচ্ছি এখানে :
বাংলা সাহিত্যে ষাটের দশকের হাংরি জেনারেশনের ন্যায় আর কোনও আন্দোলন তার পূর্বে হয় নাই । হাজার বছরের বাংলা ভাষায় এই একটিমাত্র আন্দোলন যা কেবল সাহিত্যের নয় সম্পূর্ণ সমাজের ভিত্তিতে আঘাত ঘটাতে পেরেছিল, পরিবর্তন আনতে পেরেছিল। পরবর্তীকালে তরুণ সাহিত্যিক ও সম্পাদকদের সাহস যোগাতে পেরেছে ।
১ ) হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো তাঁরা সাহিত্যকে পণ্য হিসাবে চিহ্ণিত করতে অস্বীকার করেছিলেন । কেবল তাই নয় ; তাঁরা এক পৃষ্ঠার লিফলেট প্রকাশ করতেন ও বিনামূল্যে আগ্রহীদের মাঝে বিতরণ করতেন । তাঁরাই প্রথম ফোলডার-কবিতা, পোস্ট-কার্ড কবিতা, ও পোস্টারে কবিতা ও কবিতার পংক্তির সূত্রপাত করেন । পোস্টার এঁকে দিতেন অনিল করঞ্জাই ও করুণানিধান মুখোপাধ্যায় । ফোলডারে স্কেচ আঁকতেন সুবিমল বসাক । ত্রিদিব মিত্র তাঁর ‘উন্মার্গ’ পত্রিকার প্রচ্ছদ নিজে আঁকতেন। পরবর্তীকালে দুই বাংলাতে তাঁদের প্রভাব পরিলক্ষিত হয় ।
২ ) হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ অবদান প্রতিষ্ঠানবিরোধিতা । তাঁদের আগমনের পূর্বে প্রতিষ্ঠানবিরোধিতা করার কথা সাহিত্যকরা চিন্তা করেন নাই । সুভাষ ঘোষ বলেছেন প্রতিষ্ঠানবিরোধিতার অর্থ সরকার বিরোধিতা নয়, সংবাদপত্র বিরোধিতা নয় ; হাংরি জেনারেশনের বিরোধ প্রচলিত সাহিত্যের মৌরসি পাট্টাকে উৎখাত করে নবতম মূল্যবোধ সঞ্চারিত করার । নবতম শৈলী, প্রতিদিনের বুলি, পথচারীর ভাষা, ছোটোলোকের কথার ধরণ, ডিকশন, উদ্দেশ্য, শব্দ ব্যবহার, চিন্তা ইত্যাদি । পশ্চিমবঙ্গে বামপন্হী সরকার সত্বেও বামপন্হী কবিরা মধ্যবিত্ত মূল্যবোধ থেকে নিষ্কৃতি পান নাই । শ্রমিকের কথ্য-ভাষা, বুলি, গালাগাল, ঝগড়ার অব্যয় তাঁরা নিজেদের রচনায় প্রয়োগ করেন নাই । তা প্রথম করেন হাংরি জেনারেশনের কবি ও লেখকগন ; উল্লেখ্য হলেন অবনী ধর, শৈলেশ্বর ঘোষ, সুবিমল বসাক, ত্রিদিব মিত্র প্রমুখ । সুবিমল বসাকের পূর্বে ‘বাঙাল ভাষায়’ কেউ কবিতা ও উপন্যাস লেখেন নাই। হাংরি জেনারেশনের পরবর্তী দশকগুলিতে লিটল ম্যাগাজিনের লেখক ও কবিদের রচনায় এই প্রভাব স্পষ্ট ।
৩ ) হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের তৃতীয় অবদান কবিতা ও গল্প-উপন্যাসে ভাষাকে ল্যাবিরিনথাইন করে প্রয়োগ করা । এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ মলয় রায়চৌধুরীর কবিতা ও গল্প-উপন্যাস । মলয় রায়চৌধুরী সর্বপ্রথম পশ্চিমবাংলার সমাজে ডিসটোপিয়ার প্রসঙ্গ উথ্থাপন করেন । বামপন্হীগণ যখন ইউটোপিয়ার স্বপ্ন প্রচার করছিলেন সেই সময়ে মলয় রায়চৌধুরী চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন ডিসটোপিয়ার দরবারি কাঠামো ।উল্লেখ্য তাঁর নভেলা ‘ঘোগ’, ‘জঙ্গলরোমিও’, গল্প ‘জিন্নতুলবিলদের রূপকথা’, ‘অরূপ তোমার এঁটোকাঁটা’ ইত্যাদি । তিনি বর্ধমানের সাঁইবাড়ির ঘটনা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের ‘ক্ষুধিত পাষাণ’ অবলম্বনে লেখেন ‘আরেকবারে ক্ষুধিত পাষাণ’ । বাঙাল ভাষায় লিখিত সুবিমল বসাকের কবিতাগুলিও উল্লেখ্য । পরবর্তী দশকের লিটল ম্যাগাজিনের কবি ও লেখকদের রচনায় এই প্রভাব সুস্পষ্ট ।
৪ ) হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের চতুর্থ অবদান হলো পত্রিকার নামকরণে বৈপ্লবিক পরিবর্তন । হাংরি জেনারেশনের পূর্বে পত্রিকাগুলির নামকরণ হতো ‘কবিতা’, ‘কৃত্তিবাস’, ‘উত্তরসূরী’, ‘শতভিষা’, ‘পূর্বাশা’ ইত্যাদি যা ছিল মধ্যবিত্ত মূল্যবোধের বহিঃপ্রকাশ । হাংরি জেনারেশন আন্দোলনকারীগণ পত্রিকার নামকরণ করলেন ‘জেব্রা’, ‘জিরাফ’, ‘ধৃতরাষ্ট্র’, ‘উন্মার্গ’, ‘প্রতিদ্বন্দী’ ইত্যাদি । পরবর্তীকালে তার বিপুল প্রভাব পড়েছে । পত্রিকার নামকরণে সম্পূর্ণ ভিন্নপথ আবিষ্কৃত হয়েছে ।
৫ ) হাংরি জেনারেশন আন্দোলনে সর্বপ্রথম সাবঅলটার্ন অথবা নিম্নবর্গের লেখকদের গুরুত্ব প্রদান করতে দেখা গিয়েছিল । ‘কবিতা’, ‘ধ্রুপদি’, ‘কৃত্তিবাস’, ‘উত্তরসূরী’ ইত্যাদি পত্রিকায় নিম্নবর্গের কবিদের রচনা পাওয়া যায় না । হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের বুলেটিনগুলির সম্পাদক ছিলেন চাষি পরিবারের সন্তান হারাধন ধাড়া । সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়সহ তৎকালীন কবিরা তাঁর এমন সমালোচনা করেছিলেন যে তিনি এফিডেভিট করে ‘দেবী রায়’ নাম নিতে বাধ্য হন । এছাড়া আন্দোলনে ছিলেন নিম্নবর্গের চাষী পরিবারের শম্ভু রক্ষিত, তাঁতি পরিবারের সুবিমল বসাক, জাহাজের খালাসি অবনী ধর, মালাকার পরিবারের নিত্য মালাকার ইত্যাদি । পরবর্তীকালে প্রচুর সাবঅলটার্ন কবি-লেখকগণকে বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে দেখা গেল।
৬ ) হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের ষষ্ঠ গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব হলো রচনায় যুক্তিবিপন্নতা, যুক্তির কেন্দ্রিকতা থেকে মুক্তি, যুক্তির বাইরে বেরোনোর প্রবণতা, আবেগের সমউপস্হিতি, কবিতার শুরু হওয়া ও শেষ হওয়াকে গুরুত্ব না দেয়া, ক্রমান্বয়হীনতা, যুক্তির দ্বৈরাজ্য, কেন্দ্রাভিগতা বহুরৈখিকতা ইত্যাদি । তাঁদের আন্দোলনের পূর্বে টেক্সটে দেখা গেছে যুক্তির প্রাধান্য, যুক্তির প্রশ্রয়, সিঁড়িভাঙা অঙ্কের মতন যুক্তি ধাপে-ধাপে এগোতো, কবিতায় থাকতো আদি-মধ্য-অন্ত, রচনা হতো একরৈখিক, কেন্দ্রাভিগ, স্বয়ংসম্পূর্ণতা ।
৭) হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের পূর্বে লেখক-কবিগণ আশাবাদে আচ্ছন্ন ছিলেন মূলত কমিউনিস্ট প্রভাবে । ইউটোপিয়ার স্বপ্ন দেখতেন । বাস্তব জগতের সঙ্গে তাঁরা বিচ্ছিন্ন ছিলেন । হাংরি জেনারেশন আন্দোলনকারীগণ প্রথমবার হেটেরোটোপিয়ার কথা বললেন । হাংরি জেনারেশনের কবি অরুণেশ ঘোষ তাঁর কবিতাগুলোতে বামপন্হীদের মুখোশ খুলে দিয়েছেন। হাংরি জেনরেশনের পরের দশকের কবি ও লেখকগণের নিকট বামপন্হীদের দুইমুখো কর্মকাণ্ড ধরা পড়ে গিয়েছে, বিশেষ করে মরিচঝাঁপি কাণ্ডের পর ।
৮ ) হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের পূর্বে কবি-লেখকগণ মানেকে সুনিশ্চিত করতে চাইতেন, পরিমেয়তা ও মিতকথনের কথা বলতেন, কবির নির্ধারিত মানে থাকত এবং স্কুল কলেজের ছাত্ররা তার বাইরে যেতে পারতেন না । হাংরি জেনারেশনের লেখকগণ অফুরন্ত অর্থময়তা নিয়ে এলেন, মানের ধারণার প্রসার ঘটালেন, পাঠকের ওপর দায়িত্ব দিলেন রচনার অর্থময়তা নির্ধারণ করার, প্রচলিত ধারণা অস্বীকার করলেন । শৈলেশ্বর ঘোষের কবিতার সঙ্গে অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের কবিতার তুলনা করলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে ।
৯ ) হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের পূর্বে ‘আমি’ থাকতো রচনার কেন্দ্রে, একক আমি থাকতো, লেখক-কবি ‘আমি’র নির্মাণ করতেন, তার পূর্বনির্ধারিত মানদণ্ড থাকতো, সীমার স্পষ্টিকরণ করতেন রচনাকার, আত্মপ্রসঙ্গ ছিল মূল প্রসঙ্গ, ‘আমি’র পেডিগ্রি পরিমাপ করতেন আলোচক। হাংরি জেনারেশন আন্দোলনকারীগণ নিয়ে এলেন একক আমির অনুপস্হিতি, আমির বন্ধুত্ব, মানদণ্ড ভেঙে ফেললেন তাঁরা, সীমা আবছা করে দিলেন, সংকরায়ন ঘটালেন, লিমিন্যালিটি নিয়ে এলেন ।
১০ ) হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের পূর্বে শিরোনাম দিয়ে বিষয়কেন্দ্র চিহ্ণিত করা হতো । বিষয় থাকতো রচনার কেন্দ্রে, একক মালিকানা ছিল, লেখক বা কবি ছিলেন টাইটেল হোলডার। হাংরি জেনারেশনের লেখক-কবিগণ শিরোনামকে বললেন রুবরিক ; শিরোনাম জরুরি নয়, রচনার বিষয়কেন্দ্র থাকে না, মালিকানা বিসর্জন দিলেন, ঘাসের মতো রাইজোম্যাটিক তাঁদের রচনা, বৃক্ষের মতন এককেন্দ্রী নয় । তাঁরা বললেন যে পাঠকই টাইটেল হোলডার।
১১ ) হাংরি জেনারেশনের পূর্বে কবিতা-গল্প-উপন্যাস রচিত হতো ঔপনিবেশিক মূল্যবোধ অনুযায়ী একরৈখিক রীতিতে । তাঁদের ছিল লিনিয়রিটি, দিশাগ্রস্ত লেখা, একক গলার জোর, কবিরা ধ্বনির মিল দিতেন, সময়কে মনে করতেন প্রগতি । এক রৈখিকতা এসেছিল ইহুদি ও খ্রিস্টান ধর্মগ্রন্হের কাহিনির অনুকরণে ; তাঁরা সময়কে মনে করতেন তা একটিমাত্র দিকে এগিয়ে চলেছে । আমাদের দেশে বহুকাল যাবত সেকারণে ইতিহাস রচিত হয়েছে কেবল দিল্লির সিংহাসন বদলের । সারা ভারত জুড়ে যে বিভিন্ন রাজ্য ছিল তাদের ইতিহাস অবহেলিত ছিল । বহুরৈখিকতারে প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো ‘মহাভারত’ । হাংরি জেনারেশনের কবি-লেখকগণ একরৈখিকতা বর্জন করে বহুরৈখিক রচনার সূত্রপাত ঘটালেন । যেমন সুবিমল বসাকের ‘ছাতামাথা’ উপন্যাস, মলয় রায়চৌধুরীর দীর্ঘ কবিতা ‘জখম’, সুভাষ ঘোষের গদ্যগ্রন্হ ‘আমার চাবি, ইত্যাদি । তাঁরা গ্রহণ করলেন প্লুরালিজম, বহুস্বরের আশ্রয়, দিকবিদিক গতিময়তা, হাংরি জেনারেশনের দেখাদেখি আটের দশক থেকে কবি ও লেখকরা বহুরৈখিক রচনা লিখতে আরম্ভ করলেন ।
১২ ) হাংরি জেনারেশনের পূর্বে মনে করা হতো কবি একজন বিশেষজ্ঞ । হাংরি জেনারেশনের কবিরা বললেন কবিত্ব হোমোসেপিয়েন্সের প্রজাতিগত বৈশিষ্ট্য । পরবর্তী প্রজন্মে বিশেষজ্ঞ কবিদের সময় সমাপ্ত করে দিয়েছেন নতুন কবির দল এবং নবনব লিটল ম্যাগাজিন ।
১৩ ) ঔপনিবেশিক প্রভাবে বহু কবি নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করতেন । ইউরোপীয় লেখকরা যেমন নিজেদের ‘নেটিভদের’ তুলনায় শ্রেষ্ঠ মনে করতেন । হাংরি জেনারেশনের পূর্বে শ্রেষ্ঠ কবি, শ্রেষ্ঠ কবিতা, শ্রেষ্ঠত্ব, বিশেষ একজনকে তুলে ধরা, নায়ক-কবি, সরকারি কবির শ্রেষ্ঠত্ব, হিরো-কবি, এক সময়ে একজন বড়ো কবি, ব্র্যাণ্ড বিশিষ্ট কবি আইকন কবি ইত্যাদির প্রচলন ছিল । হাংরি জেনারেশন সেই ধারণাকে ভেঙে ফেলতে পেরেছে তাদের উত্তরঔপনিবেশিক মূল্যবোধ প্রয়োগ করে । তারা বিবেচন প্রক্রিয়া থেকে কেন্দ্রিকতা সরিয়ে দিতে পেরেছে, কবির পরিবর্তে একাধিক লেখককের সংকলনকে গুরুত্ব দিতে পেরেছে, ব্যক্তি কবির পরিবর্তে পাঠকৃতিকে বিচার্য করে তুলতে পেরেছে। সবাইকে সঙ্গে নিয়ে চলার কথা বলেছে । সার্বিক চিন্তা-চেতনা ও কৌমের কথা বলেছে । তাঁদের পরবর্তী কবি-লেখকরা হাংরি জেনারেশনের এই মূল্যবোধ গ্রহণ করে নিয়েছেন ।
১৪ ) হাংরি জেনারেশনের পূর্বে শব্দার্থকে সীমাবদ্ধ রাখার প্রচলন ছিল । রচনা ছিল কবির ‘আমি’র প্রতিবেদন । হাংরি জেনারেশনের কবি-লেখকরা বলেছেন কথা চালিয়ে যাবার কথা। বলেছেন যে কথার শেষ নেই । নিয়েছেন শব্দার্থের ঝুঁকি । রচনাকে মুক্তি দিয়েছেন আত্মমনস্কতা থেকে । হাংরি জেনারেশনের এই কৌম মূল্যবোধ গ্রহণ করে নিয়েছেন পরবর্তীকালের কবি-লেখকরা । এই প্রভাব সামাজিক স্তরে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ।
১৫ ) হাংরি জেনারেশনের পূর্ব পর্যন্ত ছিল ‘বাদ’ দেবার প্রবণতা ; সম্পাদক বা বিশেষ গোষ্ঠী নির্ণয় নিতেন কাকে কাকে বাদ দেয়া হবে । হাংরি জেনারেশনের পূর্বে সাংস্কৃতিক হাতিয়ার ছিল “এলিমিনেশন”। বাদ দেবার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংস্কৃতিকে তাঁরা নিজেদের আয়ত্বে রাখতেন । হাংরি জেনারেশনের সম্পাদকরা ও সংকলকরা জোট বাঁধার কথা বললেন । যোগসূত্র খোঁজাল কথা বললেন । শব্দজোট, বাক্যজোট, অর্থজোটের কথা বললেন । এমনকি উগ্র মতামতকেও পরিসর দিলেন । তাঁদের এই চারিত্র্যবৈশিষ্ট্য পরবর্তীকালের সম্পাদক ও সংকলকদের অবদানে স্পষ্ট । যেমন অলোক বিশ্বাস আটের দশকের সংকলনে ও আলোচনায় সবাইকে একত্রিত করেছেন । বাণিজ্যিক পত্রিকা ছাড়া সমস্ত লিটল ম্যাগাজিনের চরিত্রে এই গুণ উজ্বল ।
১৬ ) হাংরি জেনারেশনের পূর্ব পর্যন্ত একটিমাত্র মতাদর্শকে, ইজমকে, তন্ত্রকে, গুরুত্ব দেয়া হতো । কবি-লেখক গোষ্ঠীর ছিল ‘হাইকমাণ্ড’, ‘হেডকোয়ার্টার’, ‘পলিটব্যুরো’ ধরণের মৌরসি পাট্টা । হাংরি জেনারেশন একটি আন্দোলন হওয়া সত্বেও খুলে দিল বহু মতাদর্শের পরিসর, টুকরো করে ফেলতে পারলো যাবতীয় ‘ইজম’, বলল প্রতিনিয়ত রদবদলের কথা, ক্রমাগত পরিবর্তনের কথা । ভঙ্গুরতার কথা । তলা থেকে ওপরে উঠে আসার কথা । হাংরি জেনারেশনের পরে সম্পূর্ণ লিটল ম্যাগাজিন জগতে দেখা গেছে এই বৈশিষ্ট্য এবং এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রভাব ।
১৭ ) হাংরি জেনারেশনের পূর্ব পর্যন্ত দেখা গেছে ‘নিটোল কবিতা’ বা স্বয়ংসম্পূর্ণ এলিটিস্ট কবিতা রচনার ধারা । তাঁরা বলতেন রচনাকারের শক্তিমত্তার পরিচয়ের কথা । গুরুগম্ভীর কবিতার কথা । নির্দিষ্ট ঔপনিবেশিক মডেলের কথা । যেমন সনেট, ওড, ব্যালাড ইত্যাদি । হাংরি জেনারেশনের কবি লেখকগণ নিয়ে এলেন এলো-মেলো কবিতা, বহুরঙা, বহুস্বর, অপরিমেয় নাগালের বাইরের কবিতা । তাঁদের পরের প্রজন্মের সাহিত্যিকদের মাঝে এর প্রভাব দেখা গেল । এখন কেউই আর ঔপনিবেশিক বাঁধনকে মান্যতা দেন না । উদাহরণ দিতে হলে বলতে হয় অলোক বিশ্বাস, দেবযানী বসু, ধীমান চক্রবর্তী, অনুপম মুখোপাধ্যায়, প্রণব পাল, কমল চক্রবর্তী প্রমুখের রচনা ।
১৮ ) হাংরি জেনারেশনের পূর্বে ছিল স্হিতাবস্হার কদর এবং পরিবর্তন ছিল শ্লথ । হাংরি জেনারেশনের কবি ও লেখকগণ পরিবর্তনের তল্লাশি আরম্ভ করলেন, প্রযুক্তির হস্তক্ষেপকে স্বীকৃতি দিলেন । পরবর্তী দশকগুলিতে এই ভাঙচুরের বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়, যেমন কমল চক্রবর্তী, সুবিমল মিশ্র, শাশ্বত সিকদার ও নবারুণ ভট্টাচার্যের ক্ষেত্রে ; তাঁরা ভাষা, চরিত্র, ডিকশন, সমাজকাঠামোকে হাংরি জেনারেশনের প্রভাবে গুরুত্ব দিতে পারলেন ।
১৯ ) হাংরি জেনারেশনের পূর্বে নাক-উঁচু সংস্কৃতির রমরমা ছিল, প্রান্তিককে অশোভন মনে করা হতো, শ্লীল ও অশ্লীলের ভেদাভেদ করা হতো, ব্যবধান গড়ে ভেদের শনাক্তকরণ করা হতো । হাংরি জেনারেশনের কবি ও লেখকরা সংস্কৃতিকে সবার জন্য অবারিত করে দিলেন । বিলোপ ঘটালেন সাংস্কৃতিক বিভাজনের । অভেদের সন্ধান করলেন । একলেকটিকতার গুরুত্বের কথা বললেন । বাস্তব-অতিবাস্তব-অধিবাস্তবের বিলোপ ঘটালেন । উল্লেখ্য যে বুদ্ধদেব বসু মলয় রায়চৌধুরীকে তাঁর দ্বারে দেখামাত্র দরোজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন । পরবর্তীকালের লিটল ম্যাগাজিনে আমরা তাঁদের এই অবদানের প্রগাঢ় প্রভাব লক্ষ্য করি ।
২০ ) হাংরি জেনারেশনের পূর্বে ছিল ইউরোপ থেকে আনা বাইনারি বৈপরীত্য যা ব্রিটিশ খ্রিস্টানরা হা্রণ করেছিল তাদের ধর্মের ঈশ্বর-শয়তান বাইনারি বৈপরীত্য থেকে । ফলত, দেখা গেছে ‘বড় সমালোচক’ ফরমান জারি করছেন কাকে কবিতা বলা হবে এবং কাকে কবিতা বলা হবে না ; কাকে ‘ভালো’ রচনা বলে হবে এবং কাকে ভালো রচনা বলা হবে না ; কোন কবিতা বা গল্প-উপন্যাস উতরে গেছে এবং কোনগুলো যায়নি ইত্যাদি । হাংরি জেনারেশনের কবি ও লেখকরা এই বাইনারি বৈপরীত্য ভেঙে ফেললেন । তাঁরা যেমন ইচ্ছা হয়ে ওঠা রচনার কথা বললেন ও লিখলেন, যেমন সুভাষ ঘোষের গদ্যগ্রন্হগুলি । হাংরি জেনারেশনের কবি ও লেখকগণ গুরুত্ব দিলেন বহুপ্রকার প্রবণতার ওপর, রচনাকারের বেপরোয়া হবার কথা বললেন, যেমন মলয় রায়চৌধুরী, পদীপ চৌধুরী ও শৈলেশ্বর ঘোষের কবিতা । যেমন মলয় রায়চৌধুরীর ‘প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার’ কবিতা ও ‘অরূপ তোমার এঁটোকাঁটা’ উপন্যাস । যেমন সুবিমল বসাকের বাঙাল ভাষার কবিতা যা এখন বাংলাদেশের ব্রাত্য রাইসুও অনুকরণ করছেন । হাংরি জেনারেশনের পরের দশকগুলিতে তাঁদের এই অবদানের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, এবং তা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের লিটল ম্যাগাজিনগুলিতে ।
২১ ) হাংরি জেনারেশনের পূর্বে ছিল আধিপত্যের প্রতিষ্ঠার সাহিত্যকর্ম । উপন্যাসগুলিতে একটিমাত্র নায়ক থাকত । হাংরি জেনারেশনের কবি ও লেখকগণ আধিপত্যের বিরোধিতা আরম্ভ করলেন তাঁদের রচনাগুলিতে । বামপন্হী সরকার থাকলেও তাঁরা ভীত হলেন না । হাংরি জেনারেশনের পূর্বে সেকারণে ছিল খণ্ডবাদ বা রিডাকশানিজমের গুরুত্ব । হাংরি জেনারেশনের কবি ও লেখকগণ গুরুত্ব দিলেন কমপ্লেকসিটিকে, জটিলতাকে, অনবচ্ছিন্নতার দিকে যাওয়াকে । যা আমরা পাই বাসুদেব দাশগুপ্ত, সুবিমল বসাক, মলয় রায়চৌধুরী, সুভাষ ঘোষ প্রমুখের গল্প-উপন্যাসে । পরবর্তী দশকগুলিতে দুই বাংলাতে এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয় ।
২২ ) হাংরি জেনারেশনের পূর্বে গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল গ্র্যাণ্ড ন্যারেটিভকে । হাংরি জেনারেশনের কবি লেখকগণ গুরুত্ব দিলেন মাইক্রো ন্যারেটিভকে, যেমন সুবিমল বসাকের ‘দুরুক্ষী গলি’ নামক উপন্যাসের স্বর্ণকার পরিবার, অথবা অবনী ধরের খালাসি জীবন অথবা তৎপরবতী কঠিন জীবনযাপনের ঘটনানির্ভর কাহিনি । পরবর্তী দশকগুলিতে দেখা যায় মাইক্রোন্যারেটিভের গুরুত্ব, যেমন গ্রুপ থিয়েটারগুলির নাটকগুলিতে ।
২৩ ) হাংরি জেনারেশনের কবি ও লেখকগণ নিয়ে এলেন যুক্তির ভাঙন বা লজিকাল ক্র্যাক, বিশেষত দেবী রায়ের প্রতিটি কবিতায় তার উপস্হিতি পরিলক্ষিত হয় । পরের দশকের লেখক ও কবিদের রচনায় লজিকাল ক্র্যাক অর্থাৎ যুক্তির ভাঙন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে । যেমন সাম্প্রতিক কালে অগ্নি রায়, রত্নদীপা দে ঘোষ, বিদিশা সরকার, অপূর্ব সাহা, সীমা ঘোষ দে, সোনালী চক্রবর্তী, আসমা অধরা, সেলিম মণ্ডল, জ্যোতির্ময় মুখোপাধ্যায়, পাপিয়া জেরিন, প্রমুখ ।
২৪ ) হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের পূর্বে রচনায়, বিশেষত কবিতায়, শিরোনামের গুরুত্ব ছিল ; শিরোনামের দ্বারা কবিতার বিষয়কেন্দ্রকে চিহ্ণিত করার প্রথা ছিল । সাধারণত বিষয়টি পূর্বনির্ধারিত এবং সেই বিষয়ানুযায়ী কবি কবিতা লিখতেন । শিরোনামের সঙ্গে রচনাটির ভাবগত বা দার্শনিক সম্পর্ক থাকতো । ফলত তাঁরা মৌলিকতার হামবড়াই করতেন, প্রতিভার কথা বলতেন, মাস্টারপিসের কথা বলতেন ।হাংরি জেনারেশন আন্দোলনকারীগণ শিরোনামকে সেই গুরুত্ব থেকে সরিয়ে দিলেন । শিরোনাম আর টাইটেল হোলডার রইলো না । শিরোনাম হয়ে গেল ‘রুবরিক’ । তাঁরা বহু কবিতা শিরোনাম র্বজন করে সিরিজ লিখেছেন । পরবর্তী দশকের কবিরা হাংরি জেনারেশনের এই কাব্যদৃষ্টির সঙ্গে একমত হয়ে কবিতার শিরোনামকে গুরুত্বহীন করে দিলেন ; সম্পূর্ণ কাব্যগণ্হ প্রকাশ করলেন যার একটিতেও শিরোনাম নেই ।
চার
দেবেশ রায় প্রথম বলেছিলেন যে হাংরি আন্দোলন থেকে নকশাল আন্দোলনের দিকে সময় একটা বীক্ষার মাধ্যমে প্রসারিত হয়েছিল, কিংবা এই ধরণের কোনো কথা, তারপর অনেকেই নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে হাংরি আন্দোলনের ভাবনার একটা যোগসূত্র খুঁজতে চেয়েছেন । সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে রফিক উল ইসলাম জিগ্যেস করেছিলেন যে দুটো আন্দোলনের নিজেদের মধ্যে কোনো সম্পর্ক আছে কিনা । সুনীল বলেছিলেন যে নকশাল আন্দোলনে অনেক মহৎ আত্মত্যাগ হয়েছিল, অনেক তরুণ মারা গিয়েছিল ।
আমার মতে দুটোর মধ্যে যে সম্পর্ক ছিল তা সময়-পরিসরের রেশের । হাংরি আন্দোলনের চিত্রকর অনিল করঞ্জাই আর করুণানিধান মুখোপাধ্যায় নকশাল আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন আর পুলিশ ওনাদের রাতের মিটিঙের কথা জানতে পেরে স্টুডিও ভাঙচুর করে যাবতীয় পেইনটিঙ নষ্ট করে দিয়েছিল । অনিল, করুণা আর ওদের ছবি আঁকার দলের যুবকরা আগেই খবর পেয়ে শহর ছেড়ে চলে গিয়েছিল, অনিল দিল্লিতে আর তারপর এক মার্কিন যুবতীর সঙ্গে আমেরিকায় ; করুণা চুলদাড়ি কামিয়ে, চেহারা পালটিয়ে সপরিবারে পাটনায়, সেখানে দাদা করুণাকে একটা রঙিন মাছের দোকান খুলে দিয়েছিলেন । আমার কাকার মেয়ে পুটি উত্তরপাড়ার বাড়ির বড়োঘরের কড়িকাঠ থেকে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়েছিল, তার কারণ যে নকশাল যুবকটিকে পুটি ভালোবাসতো তাকে পুলিশ তুলে নিয়ে গিয়ে লোপাট করে দিয়েছিল ।
ব্যাঙ্কশাল কোর্টে আমার এক মাসের সাজা হয়ে গিয়েছিল ২৮ ডিসেম্বর ১৯৬৫ আর কলকাতা হাইকোর্টে উকিলের খোঁজে আমি নানা লোকের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করছিলুম । জ্যোতির্ময় দত্ত পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন সদ্য লণ্ডন ফেরা ব্যারিস্টার করুণাশঙ্কর রায়ের সঙ্গে, ব্যাঙ্কশাল কোর্ট থেকে কপি নিয়ে যাবতীয় কাগজপত্র দিয়ে আসতে হচ্ছিল, তাঁর বাড়িতে, লোহাপট্টিতে, যাতে কলকাতা হাইকোর্টে রেজিস্ট্রারের দপতরে জমা দেয়া যায় । এদিকে কলকাতায় আমার মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই, নানা জায়গায় রাত কাটাই, পকেট ফাঁকা হয়ে যায় আদালতের কাজে আর দুবেলা খেতে । অনেককাল স্নান না করলে যে নিজের গা থেকে নিজেরই মাংসের গন্ধ বেরোয় তা তখন জেনেছিলুম । বন্ধুবান্ধবরা, সুবিমল বসাক ছাড়া, সবাই হাওয়া ।
তার মাঝেই ২২-২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৬৬ খাদ্য আন্দোলনে সারা বাংলা বন্ধ ডাকা হয়েছিল, মনে আছে । তখনকার কলেজ স্ট্রিট এখনকার মতন ছিল না, একেবারে ফাঁকা থাকতো, দিনের বেলাকার মিছিল সত্বেও, সন্ধ্যে হলেই অন্ধকার । বস্তুত, পুরো কলকাতাই একেবারে আলাদা ছিল । রণবীর সমাদ্দারের একটা লেখায় পড়েছিলুম যে নকশাল আন্দোলনের প্রকৃত সময়টা হলো ১৯৬৭ থেকে ১৯৭০ ; আর কোলকাতা হাইকোর্ট আমার মামলা এক দিনেই সেরে ফেলেছিল, ২৬ জুলাই ১৯৬৭ তারিখে, আমার দণ্ডাদেশ নাকচ করে । তাই হয়তো কেউ-কেউ মনে করেন যে হাংরিরা ১৯৬৭-পরবর্তী কালখণ্ডকে নকশালদের হ্যাণ্ডওভার করে দিয়েছিল । সময়-পরিসরকে হ্যাণ্ডওভার করার প্রক্রিয়া চলে আসছে সেই ব্রিটিশ-বিরোধিতার সময় থেকে। প্রফুল্ল চক্রবর্তী ওনার ‘মার্জিনাল মেন’ বইতে লিখেছিলেন যে দেশভাগের পর বহু তরুণ লুম্পেন প্রলেতারিয়েত হয়ে ওঠে এবং তাদের থেকেই পশ্চিমবঙ্গে মাস্তানদের জন্ম । বস্তুত মাস্তানরও সময়-পরিসরকে ক্রমশ হ্যাণ্ডওভার করে চলেছে এখনকার জিঙ্গোবাদী রাজনীতিকদের করকমলে ।
ঔপনিবেশিক কালখণ্ডে স্বদেশি আন্দোলনের যে রেশ আরম্ভ হয়েছিল, সেই রেশ নানা বাঁক নিয়ে যখন দেশভাগের ঘুর্ণিতে পড়ল তখন তার চরিত্র পালটে গেল, তার আগে সেই রেশে তেমন অ্যাড্রেনালিন ছিল না বলা চলে । এই রেশটাই হাংরি আন্দোলনের উৎসভূমি । এই রেশকে প্রথমে কৃষক নেতারা এবং পরে তরুণ সমাজ নিয়ে যান নকশাল আন্দোলনে এবং এই রেশকেই কেন্দ্র করে বামপন্হীরা পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আসেন। এই রেশই নন্দীগ্রামে পৌঁছোবার পর বামপন্হীরা দিশেহারা হয়ে পড়েন আর তৃণমূল ক্ষমতা দখল করে । রেশটা থাকে জনগণের মাঝে । আমার মনে হয়, সব সময়েই থাকে,চিরকাল থাকে ।
হাংরি আন্দোলনের পরে-পরেই নকশাল আন্দোলন ঘটেছিল অথচ যাঁরা হাংরি আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে প্রশাসন ও পুলিশের কাছে নালিশ করেছিলেন তাঁরা কেন আসন্ন উথালপাথাল টের পাননি ? হাংরি আন্দোলনকারীরা সাহিত্যজগতের মূল্যবোধ-মালিক ও প্রকাশক-বাজারের জোতদারদের উৎখাত করতে চেয়েছিল, জন্তুজানোয়ারের মুখোশ পাঠিয়ে বিদ্যায়তনিক জোতদারদের টপলেস অর্থাৎ গলা কেটে ফেলতে চেয়েছিল, সাহিত্যিক ক্ষমতাকে দখল করে বিলিয়ে দিতে চেয়েছিল লিটল ম্যাগাজিনের মাঝে, জুতোর বাক্স রিভিউ করতে দিয়ে এবং শাদা ফুলস্কেপ কাগজকে ছোটোগল্প নামে বাজারি কাগজে জমা দিয়ে সাহিত্যিক জোতদারদের দলিদস্তাবেজ বেদখল করতে চেয়েছিল । এগুলো কোনোরকমের ইয়ার্কি বা প্র্যাঙ্ক ছিল না।
যাঁরা নালিশ ঠুকেছিলেন তাঁদের মধ্যে বিদ্যায়তনিক প্রতিনিধিরাও ছিলেন যাঁদের হাংরি আন্দোলনকারীদের পাঠানো কার্ডে FUCK THE BASTARDS OF GANGSHALIK SCHOOL OF POETRY ঘোষণা পড়ে অপমানবোধ হয়েছিল, জানোয়ার ও দানবের মুখোশ পেয়ে মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল । অথচ তার কয়েক বছর পরেই নকশাল তরুণরা শিক্ষকদের গলা কাটা আরম্ভ করলেন, জোতদারদের বাড়ি লুঠ করে দলিল-দস্তাবেজ পুড়িয়ে দিলেন, জমি দখল করে বিলিয়ে দিলেন ভাগচাষিদের । নকশাল আন্দোলনকারীরা জোতদারদের বেদখল করার সময়ে, বাড়িতে-খামারে আগুন ধরিয়ে দেবার সময়ে FUCK THE BASTARDS -এর পরিবর্তে বাংলা ও চোস্ত হিন্দি গালাগাল দিয়েছিল, জোতদার আর ভূস্বামীদের মুখোশ চামড়াসুদ্দু ছিঁড়ে উপড়ে নিয়েছিল ।
নকশাল তরুণরা এসে দেখিয়ে দিল যে হাংরি আন্দোলনকারীদের এই কাজগুলো ঠাট্টা-ইয়ার্কি করার ব্যাপার ছিল না, তা ছিল চোখে আঙুল ঢুকিয়ে বাস্তবের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার প্রক্রিয়া । জোতদারদের বিরুদ্ধে যে ইতর বুলি কথাবার্তায় প্রয়োগ করে ক্ষান্ত থেকেছিলেন নকশালরা, তা নিজেদের লেখায় নিয়ে এসেছিলেন হাংরি আন্দোলনকারীরা যাকে মধ্যবিত্ত পরিবারের বিদ্যায়তনিক ও গ্লসি পত্রিকার চাকুরে আলোচনাকারীরা বলে এসেছেন অশ্লীল ও অশোভন । আলোচকরা ভুলে গিয়েছিলেন যে ছোটোলোকদের ভাষা অমনই হয়। নকশাল আন্দোলনের কবিতা কিন্তু মধ্যবিত্ত বাঙালির ভাষার আওতার বাইরে বেরোতে পারেনি বলেই মনে হয় ।
যেমন কৃষ্ণ ধর-এর ‘একদিন সত্তর দশকে’ কবিতাটি :-
শিকারকে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে
অন্ধকারে মিলিয়ে যায় জল্লাদের গাড়ি
শহরের দেয়ালে দেয়ালে পরদিন দেখা যায় তারই কথা
সে নিদারুণ তৃষ্ণায় একবার জল চেয়েছিল
যে যন্ত্রণায় নীল হয়ে একবার ডেকেছিল মাকে
তবু স্বপ্নকে অক্ষত রেখেই সে
বধ্যভূমিতে গিয়েছিল
একদিন সত্তর দশকে।”
স্বপন চক্রবর্তী লিখেছিলেন :-
‘আমরা সাহায্য চাইনি’
আমরা সাহায্য চাইনি
কারণ আমরা বদল চেয়েছি।
চেয়েছি ক্ষিদের মানসিক যন্ত্রণার বিরুদ্ধে
একটি সকাল, দুপুর, রাত সময়, কাল, অনন্ত সময়।
.কোনদিনই আমরা কমিউনিস্ট হতে চাইনি।
এখন সময়
মানুষের জন্যে আমাদের মানুষের মত হতে শেখাচ্ছে।
মানুষের জন্যে আমাদের মানুষের মত হতে শেখাচ্ছে।
আমরা চাইনি ইজ্জত খুইয়ে ঘাড় হেঁট করে পেট ভরাতে।
আমরা বদল চেয়েছি
চেয়েছি ক্ষিদের যন্ত্রণার বিরুদ্ধে
একটি সকাল, দুপুর, রাত সময়, কাল, অনন্ত সময়।”
নির্মল ঘোষ তার ‘নকশালবাদী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য’ গ্রন্থে লিখেছেন, ‘অনস্বীকার্য, নকশালপন্থী কাব্যচর্চায় আঙ্গিকের চেয়ে বিষয়কেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। আর এর ফলে বক্তব্যে বহুক্ষেত্রেই আবেগের প্রাধান্য দেখা গেল, যা শেষপর্যন্ত পাঠক মানসকে প্রায়শ প্রভাবিত বা প্রাণিত করতে সমর্থ হয়নি।’ পক্ষান্তরে, কবিতার শৈল্পিক মানের এ বিতর্কে অর্জুন গোস্বামী নকশালবাদী কবিতার পক্ষেই রায় দিয়েছেন, ‘এটা সত্তরের দশক। এই দশক প্রত্যক্ষ করেছে শোষকশ্রেণীর বিরুদ্ধে শোষিতশ্রেণীর লড়াই। এই দশকেই প্রমাণিত হয়েছে যে প্রতিক্রিয়াশীল শাসকচক্রকে উপরে উপরে যতই শক্তিশালী বলে মনে হোক না কেন আসলে তারা হলো কাগুজে বাঘ। স্বভাবতই এই দশকের মানুষের সচেতনতা অনেক বেশি। আমরা এমন কোন কবিতা পড়তে চাই না যাতে আছে হতাশা, আছে যন্ত্রণার গোঙানি। আমরা এমন কবিতা পড়তে চাই যাতে ধরা পড়বে শোষণের আসল স্বরূপ, যে কবিতা পড়ে অনুপ্রেরণা পাবেন লক্ষ লক্ষ খেটে খাওয়া মানুষ এবং যে কবিতা প্রকৃতই হবে শোষিতশ্রেণীর সংগ্রামী হাতিয়ার। আমাদের মধ্যে অনেকে বলেন কবিতা হলো এমন একটা জিনিস যা ঠিক স্লোগান নয়। আমাদের বক্তব্য হলো কবিতার বিষয় ও কবিতার আঙ্গিক এই দুটোর মধ্যে আগে বিষয়, পরে আঙ্গিক। বক্তব্যকে সাধারণের উপযোগী করে বলার জন্য কবিতা যদি কারুর কাছে স্লোগান বলে মনে হয় তবে সেই স্লোগানই হলো সত্তরের দশকের শ্রেষ্ঠ কবিতা।’
হাংরি আন্দোলনের সময়ে আমিও বলেছিলুম, “কবিতা কেবল মঞ্চে বিড়-বিড় করে পড়ার ব্যাপার নয় ; উন্মাদের মতন চিৎকার করে না পড়লে প্রতিষ্ঠান কষ্ট-যন্ত্রণার গোঙানি শুনতে পায় না ।” বাসব রায়কে দেয়া ‘যুগশঙ্খ’ পত্রিকার সাক্ষাৎকারে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বলেছিলেন যে মলয়ের কবিতায় অত্যধিক অব্যয় থাকে, চিৎকার থাকে । এই প্রেক্ষিতে নকশালদের সঙ্গে হাংরিদের তুলনা করা চলে, যেমন ত্রিদিব মিত্রের বিখ্যাত কবিতা ‘হত্যাকাণ্ড’ । হাওড়া স্টেশানের প্ল্যাটফর্মে বেঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে ‘হত্যাকাণ্ড’ কবিতাটা পড়ে ভিড় জমিয়ে ফেলেছিল ত্রিদিব মিত্র ।
হাংরি আন্দোলনের গ্রন্হ রিভিউ করতে গিয়ে শৈলেন সরকার বলেছেন, “হাংরি-র পুরনো বা নতুন সব কবি বা লেখকই কিন্তু অনায়াসে ব্যবহার করেছেন অবদমিতের ভাষা। এঁদের লেখায় অনায়াসেই চলে আসে প্রকৃত শ্রমিক-কৃষকের দৈনন্দিন ব্যবহৃত শব্দাবলি। ভালবাসা-ঘৃণা বা ক্রোধ বা ইতরামি প্রকাশে হাংরিদের কোনও ভণ্ডামি নেই, রূপক বা প্রতীক নয়, এঁদের লেখায় যৌনতা বা ইতরামির প্রকাশে থাকে অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষ বিবরণ— একেবারে জনজীবনের তথাকথিত শিল্পহীন কথা। অনেকেই প্রায় সমসময়ের নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে হাংরি আন্দোলনকে তুলনা করে এদের অরাজনৈতিক তকমা দেন, কিন্তু ক্ষমতার সঙ্গে ভাষার সম্পর্ক নিয়ে হাংরি জেনারেশন যে প্রশ্ন তুলেছিল তা ছিল নকশালদের তোলা প্রশ্নের চেয়েও অনেক বেশি মৌলিক। এমনকী তুমুল প্রচার পাওয়া এবং নিজস্ব অস্তিত্ব তৈরি করা সত্ত্বেও দলিত সাহিত্য আন্দোলনকে শেষ পর্যন্ত হাংরি আন্দোলনের থেকে পিছিয়েই রাখতে হয়।” শৈলেন সরকার যে বইটি আলোচনা করেছেন তাতে কোনো কারণে সম্পাদকমশায় হাংরি আন্দোলনের রাজনৈতিক ম্যানিফেস্টো অন্তর্ভুক্ত করেননি । করলে স্পষ্ট হতো যে হাংরি আন্দোলন অরাজনৈতিক ছিল না ।
প্রবুদ্ধ ঘোষ হাংরি আন্দোলন ও নবারুণ ভট্টাচার্য সম্পর্কে আলোচনা করার সময়ে বলেছেন, “বাড়ি ভেঙ্গে পড়ার শব্দ তখনই শোনা যায়, যখন তা শোনার জন্যে কেউ থাকে। সাহিত্যের কাজ কী? ক্যাথারসিস করা? মানে, মোক্ষণ? বরং হাংরিদের লেখা প্রতিমুহূর্তে ক্যাথারসিসের উল্টোদিকে হাঁটে। মোক্ষণ করা, শান্তি দেওয়া তাঁদের কাজ নয়, বরং আপাতশান্তির বোধটাকে আঘাত করাই মূল উদ্দেশ্য!” একটু আগে আমি যেকথা বলেছি, অর্থাৎ প্রতিষ্ঠান-সাহিত্যের জোতদারদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলতে চেয়েছিল হাংরি আন্দোলনকারীরা, তাদের কাজের দ্বারা, লেখার দ্বারা, ড্রইং দ্বারা, সেকথাই বলেছেন প্রবুদ্ধবাবু । তবে প্রবুদ্ধবাবু একটা কথা ভুল বলেছেন, যে হাংরি আন্দোলনকারীরা কেবল আত্মবীক্ষণ ও আত্মআবিষ্কারে আলো ফেলতে চেয়েছেন। হাংরি আন্দোলনকরীরা যদি তাই করতেন তাহলে যে কাজগুলোকে মধ্যবিত্ত আলোচকরা ‘অসাহিত্যিক’ ব্যাপার বলে তকমা দেগে দেন তা তাঁরা করতেন না, বিভিন্ন বিষয়ে ম্যানিফেস্টো প্রকাশ করতেন না । নকশালরা যে মূর্তির গলা কেটে প্রতীকিস্তরে বিশেষ মূল্যবোধকে আক্রমণ করেছিল, শিক্ষকদের খুন করেছিল, তার সঙ্গে হাংরি আন্দোলনের প্রাতিষ্ঠানিক মূল্যবোধ-খুনের আক্রমণাত্মক কাজগুলো তুলনীয় ।
সুবিমল বসাকের একটা কবিতা এখানে তুলে দিচ্ছি, যা হাংরি বুলেটিনে প্রকাশিত হয়েছিল :-
‘হাবিজাবি’
আমারে মাইরা ফেলনের এউগা ষড়যন্ত্র হইসে
চারো কোনা দিয়া ফুসফুস আওয়াজ কানে আহে
ছাওয়াগুলান সইরা যায় হুমকে থিক্যা
অরা আমারে এক্কেরে শ্যায করতে সায়
আমি নিজের ডাকাইতে্যা হাতেরে লইয়া সচেত্তন আসি
কেউ আইয়া চ্যারায় দিশায় চ্যাবা কথা কয় না
আমি সুপসাপ থাকি
ভালাসির গুছাইয়া আমি কথা কইতে পারি না
২ কইতে গিয়া সাত হইয়া পড়ে
১৫ সাইলে ৯ আইয়া হাজির হয়
ছ্যাব ফেলনের লাইগ্যা বিচড়াইতাসি অহন
আহ, আমার দাঁত মাজনের বুরুশ পাইতাসি না
বিশ্বাস করেন, কেউ একজনা আমার মুহের সকরা খাবার খাইসে ।
(হাংরি বুলেটিন নং ১৮ থেকে)
প্রবুদ্ধবাবু বলেছেন “হাংরিদের ‘ক্ষুধা’ বিষয়ে তাঁদের নিজস্ব মতামত ছিল ; এই ক্ষুধা আসলে নিজেকে দগ্ধ করে সত্য আবিষ্কারের ক্ষুধা। সত্য, যা ক্রমাগতঃ এমনকি নিজেকেও ছিঁড়েখুঁড়ে উন্মোচিত করে চলে। তাকাই ফাল্গুনী রায়ের কবিতায়, “আমার বুকের ভিতর লোভ অথচ হৃদয় খুঁজতে গিয়ে বুকের ভিতরে/ রক্তমাংসের গন্ধ পাচ্ছি কেবল”। আজ স্যানিটারি ন্যাপকিন নিয়ে আলোচনা হচ্ছে; প্রকাশ্যে চুম্বন করে প্রতিবাদ জানানো হচ্ছে রাষ্ট্রীয় বাধানিষেধ ও সমাজের প্রচলিত ‘ট্যাবু’গুলিকে। এই বিদ্রোহ কিন্তু ’৬০ এর দশক থেকেই শুরু করে দিয়েছিলেন ক্ষুধার্ত প্রজন্মের লেখকেরা। সমস্তরকম গোঁড়ামি এবং ‘ঢাকঢাকগুড়গুড়’ বিষয়ের ভিতে টান মেরেছেন। সাহিত্য বহু আগেই ভবিষ্যতের কোনো এক আন্দোলনের কথা স্বীকার করে যাচ্ছে- তার নিজের মত করে, নিজের প্রকাশে। না, নিশ্চিতভাবেই সাহিত্যের কাজ ভবিষ্যৎদর্শন নয়; কিন্তু হ্যাঁ, সাহিত্যের অন্যতম কাজ ভবিষ্যতের সামাজিক আন্দোলনের, সাহিত্য আন্দোলনের সূত্রগুলোর হদিশ দিয়ে যাওয়া। ফাল্গুনী রায় যখন কবিতায় বলেন, ‘শুধুই রাধিকা নয়, গণিকাও ঋতুমতী হয়’, তখন কি আজকের কথাই মনে হয় না? যেখানে, ঋতুমতী হওয়া কোনো ‘লজ্জা’র বিষয় নয়, ‘অশুদ্ধি’র বিষয় নয়, বরং তা স্বাভাবিক জৈবনিক প্রক্রিয়া। আর, প্রতিমুহূর্তের এই আত্মজৈবনিক বিষয়গুলিই উঠে আসে হাংরি জেনারেশনের লেখায়। বা, সগর্ব্ব মানুষ-প্রমাণ ‘আমি মানুষ একজন প্রেম-পেচ্ছাপ দুটোই করতে পারি’’। এগুলো তো দৈনন্দিন। এগুলো তো স্বাভাবিক। তাহলে? আসলে, ‘শুদ্ধতা’-র একটা অর্থহীন ধোঁয়াশাবোধ তো তৈরি করেই দেয় সমাজ, একটা বর্ডারলাইন। সাহিত্যের নায়ক রক্তমাংসের মতো হবে কিন্তু তার ক্ষুধা-রেচন ইত্যাদি থাকবে না বা পুরাণচরিত্রদের শারীরবৃত্তীয় কার্য নেই! এই ‘মেকি’ ধারণাসমূহ লালন করে আসা আতুপুতু প্রতিষ্ঠানগুলো যখন হাড়-মজ্জা-বোধ জীবন্ত হতে দেখে তখন ‘অশ্লীল সংস্কৃতি’ ছাপ্পা মারে। সমাজের জড়তা, মধ্যবিত্ত ভণ্ডামির মুখোশগুলো খুলে দেয় টান মেরে। আর, তাই ‘নিষিদ্ধ’, অশ্লীল মনে হয় এদের লেখাগুলি। হাংরি-দের যেখানে মূল বক্তব্যই ছিল প্রতিটি লেখায় ও সাহিত্যযাপনে আত্মউন্মোচন, সেখানে এই বিষয়গুলি স্বাভাবিক বীক্ষাতেই উঠে এসেছে। এবং, ‘সাহিত্য বিক্রির জন্যে আরোপিত যৌনতা’ বনাম ‘শিল্প ও জীবনের সাথে সম্পৃক্ত যৌনতা’ এই বিতর্কের ডিস্কোর্স তৈরি করেছে।”
প্রবুদ্ধবাবু আরও বলেছেন, “পণ্যসময়ে বেঁচে থেকে, কিচ্ছু না-পেয়ে বেঁচে থেকে, হতাশার অবিমৃষ্য বোধ তৈরি হয়। ’৬০-’৭০ র দশকের ক্রমাগত অর্থনৈতিক অবক্ষয়, মধ্যবিত্তের আশাহীনতার অভিঘাত নৈরাশ্যের জন্ম দেয়; এমনকি সাহিত্যেও। আর, সেই নৈরাশ্যকে এড়িয়ে গিয়ে কবিতা বা গদ্য লেখা যায় না। অরুণেশ ঘোষ তাঁর ‘কিচ্ছু নেই’ সময়কে লিখছেন- ‘১ পাগল এই শহরের চূড়ায় উড়িয়ে দিয়েছে তার লেঙ্গট/ ১ সিফিলিস রুগী পতাকা হাতে মিছিলের আগে/ ১ রোবট নিজেকে মনে করে আগামীকালের শাসক/ ১ মূর্খ ঘুমিয়ে থাকে শহর-শুদ্ধ জেগে ওঠার সময়... শীতের ভোর রাত্রে- মধ্যবিত্তের স্বপ্নহীনতার ভেতর/ আমাকে দেখে হো হো করে হেসে ওঠে বেশ্যাপাড়ার মেয়েরা’। এই স্বপ্নহীনতাকে বাড়িয়ে তোলে পুঁজিবাদের দমবন্ধ চেপে বসা। ভারতের তথা বাংলার অর্থনীতি-মডেলকে সাজানোর দোহাই দিয়ে বিদেশি শস্যবীজ এবং সবুজ বিপ্লবের সাথেই আমদানি হয় পুঁজিবাদী ব্যবস্থা। আর, নগরায়ণের মুখ খুলতে থাকে। ’৯০ র দশকের পরে যে বীভৎস হাঁ-তে ঢুকে যেতে থাকবে ভারতবর্ষের একের পর এক গ্রাম-মফস্বল।”
১৯৬৮ সালে বিনয় ঘোষ ‘কলকাতার তরুণের মন’ নামক প্রবন্ধে লিখছেন- “গোলামরা সব উঁচুদরের ঊর্ধ্বলোকের গোলাম, আগেকার কালের মতো তাঁদের হাত-পায়ের ডাণ্ডাবেড়ি দেখা যায় না। তাঁদের ‘স্টেটাস’ আছে, ‘কমফর্ট’ আছে, ‘লিবার্টি’ আছে। তাঁরা নানাশ্রেণীর ব্যুরোক্র্যাট টেকনোক্র্যাট ম্যানেজার ডিরেক্টর ইঞ্জিনিয়ার সেলস-প্রমোটার বা ‘অ্যাড-মেন’- যাঁরা যন্ত্রের মতো সমাজটাকে চালাচ্ছেন। ব্যক্তিগত ভোগ-স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাধীনতার একটা লোভনীয় মরীচিকা সৃষ্টি করছেন তাঁরা সাধারণ মানুষের সামনে এবং দিনের পর দিন বিজ্ঞাপনের শতকৌশলে নেশার পিল খাইয়ে সেই ভোগস্বাধীনতার স্বপ্নে তাদের মশগুল করে রাখছেন।”। ’৬০-’৭০ র অবক্ষয়ী অথচ পণ্যপ্রিয় ভোগসমাজের কথা সেইসময়ের মতন করেই লেখেন হাংরি আন্দোলনের গল্পকাররা। আর, ভবিষ্যতের পণ্যসমাজের একটা আভাসও থাকে। “আপাতত প্রতীয়মান ধূম্রজালে জড়ানো ধীরে ধীরে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর একজন দৈত্যভৃত্য বলে, ‘আপনার গোলাম, আকা কি হুকুম যা বলবেন যা চাইবেন জীবনে তাই হাজির... একটি সিগারেট। ...একটি সিগারেট। পাঁচ বছরে একটি টিভি সেট। দশ বছরে একটি গাড়ি আর বিশ বছরে সিগারেট খেতে খেতে একবার সারা দুনিয়ায় চক্কর দেব। বাতাস স্তব্ধ। অবাক হঠাৎ মেঘের আকাশ-কাঁপানো অট্টহাসি।”[ঘটনাদ্বয় ও তাদের সাজসজ্জাঃ রবিউল]
বোর্দ্রিয়ারের মতে, উত্তর-আধুনিক সমাজে শ্রেণিবিভাগ আর শুধুমাত্র উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত থাকছে না, বরং তা এখন নির্ভর করছে ভোগের ওপর। কে কোন পণ্য ভোগ করছে, তার ‘ব্র্যাণ্ড’ এবং দামের ওপর নির্ভর করছে তার শ্রেণিঅবস্থান। অতিরিক্ত বিজ্ঞাপন, পণ্যকৌশলে ভুলিয়ে দিতে চাওয়া দেশকাল-ইতিহাস আর, এমনকি প্রকৃত যৌনতা, সামাজিকতা, সবকিছুরই মৃত্যু ঘটছে- তখনই অধিবাস্তব টেনে নিয়ে চলেছে ‘ভার্চ্যুয়াল’ জগতে, এই সত্য তো হাংরি আন্দোলনকারীদের লেখাতে উদ্ঘাটিত হয়েছে! বস্তুতঃ, তাঁদের লেখায় তাঁরা এটাকেই আক্রমণ শানাতে চেয়েছেন। আজকের মানুষের পরিসর-মাফিক রূপবদলের কথা আমি লিখেছি আমার ‘জিন্নতুলবিলাদের রূপকথা’ নামের অধিবাস্তব গল্পে আর পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক বাস্তবতাকে ফাঁসিয়েছি ‘গহ্বরতীর্থের কুশীলব’ নামের অধিবাস্তব কাহিনিতে --- যা কিনা সময়-পরিসরের সঙ্গে অ্যাড্রেনালিনের রেশ এগিয়ে নিয়ে যাবার প্রক্রিয়া ।
হাংরি আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে মামলা-মকদ্দমা করে তাদের বিক্ষিপ্ত করে দেবার পর, প্রতিষ্ঠানের লেখকরা লেখালিখি করে দেখাতে চাইলেন, নকশাল আন্দোলন মধ্যবিত্ত রোম্যাণ্টিকতা ও কাঁচা প্রেমের মতো, বামপন্থা মানেই তা ভ্রষ্ট সমাজতন্ত্রের স্বপ্ন দেখায় এবং আসলে নিরাজনীতিই মানুষকে ‘মানুষ’ করে তোলে! হাংরিদের পর থেকে তাদের বিরুদ্ধতাকারী পঞ্চাশের ও পরবর্তী সাহিত্যিকরা এহেন ভাবনাগুলোকে সচেতন ভাবেই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে ছড়িয়ে দিতে লাগলেন । প্রবুদ্ধ ঘোষ বলেছেন “আশির দশকের বাংলা সাহিত্য থেকেই আর, ’৯০ পরবর্তী প্রাতিষ্ঠানিক ও ‘এলিট’ পত্রিকার সাহিত্যগুলি কিছু অবয়ববাদী বা স্ট্রাক্চারালিস্ট ধাঁচা (স্টিরিওটাইপ) এনে ফেলল। যেমন, নকশাল ছেলেটি লেখাপড়ায় মারাত্মক ব্রিলিয়াণ্ট ছিল, ‘ভুল’ রাজনীতির পাল্লায় পড়ে গ্রামে গেল রাজনীতি শিখতে ও ডি-ক্লাস্ড হতে, তার প্রেমিকা উচ্চবিত্ত ঘরের এবং যৌনসম্পর্কের বিশদ অনর্থক বর্ণনা, পুলিশের গুলিতে বা অত্যাচারে পঙ্গু হল, আদতে লড়াইটা এবং মতাদর্শটা ব্যর্থ হল এবং অ্যাপলিটিক্সের ওপরে সমাজসেবার ওপরে ভরসা রাখল ব্যর্থ নায়ক! এই অবয়ববাদী ধাঁচায় ফেলে প্রতিষ্ঠানগুলি বিক্রি বাড়াতে লাগল তাদের সাহিত্যের। আর, তার সাথেই ক্রমে ‘সক্রিয় রাজনীতি’ ও বামপন্থা থেকে বিমুখ করে দিতে লাগল বিশ্বায়ন পরবর্তী প্রজন্মকে।
প্রবুদ্ধবাবু বলেছেন, “হাংরি-দের গল্পের এবং গদ্যের ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ পাঠ হচ্ছে, মুক্তসমাপ্তি। অর্থাৎ, কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছেন না লেখক; হয়তো স্থির সিদ্ধান্ত হয় না কোনও। অন্ততঃ, যে সময়ে তাঁরা লিখছেন, সেই সময়ে অচঞ্চল বিশ্বাস কিছু নেই, কোনও স্থিতি নেই, সিদ্ধান্তে আসার ভিত্তি নেই। বাসুদেব দাশগুপ্তের ‘বমন রহস্য’ গল্পে আশাহীন এবং আলোহীন ভোগবাদী সমাজের প্রতি ঘৃণা ঠিকরে বেরোয়। গল্পের শেষ লাইন- “বমি করে যাই রক্তাক্ত পথের উপরে। সমস্ত চর্বিত মাংসের টুকরো, সমস্ত জীবন ভোর খেয়ে যাওয়া মাংসের টুকরো আমি বমি উগরে বার করতে থাকি। বমির তোড়ে আমার নিঃশ্বাস যেন আটকে আসে।”।
আসলে মুক্তসূচনা এবং মুক্তসমাপ্তির জনক হলেন জীবনানন্দ দাশ । ‘মাল্যবান’ যেভাবে শেষ না হয়েও শেষ হয়েছে, তা থেকে ব্যাপারটা স্পষ্ট হয় । এই শৈলী প্রয়োগে পাঠকের যথেচ্ছ স্বাধীনতা থাকে, জীবনের সাথে মিলিয়ে পরিণতি ভাবার; সিদ্ধান্তে পৌঁছে দেওয়ার দায় কবির বা লেখকের নয়। প্রবুদ্ধবাবুকে অবশ্য একথা বলার যে, নকশাল আন্দোলন বা ফিদেল কাস্ত্রোর আন্দোলনও ছিল মুক্তসমাপ্তির, আন্দোলনের পরে কি ঘটবে তা আগাম পরিকল্পনার প্রয়োজন ছিল না । নকশাল আন্দোলনকারীরা জানতেন নিশ্চয়ই যে পশ্চিমবঙ্গ বলতে ভারতবর্ষ বোঝায় না । চারু মজুমদার কি জানতেন না যে চীন আদপে তিব্বত দখল করার পর মাও-এর সাম্রাজ্যবদী দিকটাকে ফাঁস করে দিয়েছে ? এখন চীন যা করছে তার ভিত তো মাও-এর গড়ে দেয়া।
প্রবুদ্ধ ঘোষ বলেছেন, “নবারুণ কবিতার সংজ্ঞাও একপ্রকার নির্ধারণ করে দিচ্ছেন। ঠিক যেভাবে হাংরি-রা তাদের কবিতার ধারণা স্বতন্ত্র করে দিয়েছেন । নবারুণের কবিতা চিরাচরিত চাঁদ-ফুল-তারার রোম্যাণ্টিকতা অস্বীকার করে। কবিতা যে ‘লেখার’ নয়, বরং কবিতা ‘হয়ে ওঠার’ বিষয়, তা স্পষ্টতর হয় অস্থির সময়ে- “কবিতা এখনই লেখার সময়/ ইস্তাহারে দেওয়ালে স্টেনসিলে/ নিজের রক্ত অশ্রু হাড় দিয়ে/ এখনই কবিতা লেখা যায়...”। কবিতার আসন্ন সম্ভাবনাও লিখে রাখেন শেষ পংক্তিগুলিতে। “কবিতার জ্বলন্ত মশাল/ কবিতার মলোটভ ককটেল/ কবিতার টলউইন অগ্নিশিখা/ এই আগুনের আকাঙ্খাতে আছড়ে পড়ুক”। হাংরি আন্দোলনকারীরাই প্রথম বলেছিল যে কবিতা চাঁদ-ফুল-তারা ইত্যাদির ব্যাপার নয় । আমি আমার কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধে এ-কথা ষাটের দশকেই বলেছিলুম ।
প্রবুদ্ধবাবু বলেছেন, “এখানেই কবিতাকে নতুনভাবে সাজিয়ে নেওয়ার ভাবনার সাথে মিল পাওয়া যায় হাংরি-দের। ১৯৬১ সালের নভেম্বরে পাটনা থেকে প্রথম হাংরি বুলেটিন বেরোয় ইংরাজিতে। ‘Weekly manifesto of hungry generation’, যার সম্পাদক দেবী রায়, মুখ্যনেতা শক্তি চ্যাটার্জ্জী এবং ক্রিয়েটর মলয় রায়চৌধুরি। তার প্রথম অনুচ্ছেদ- “Poetry is no more a civilizing maneuver, a replanting of the bamboozled gardens; it is a holocaust, a violent and somnambulistic jazzing of the hymning five, a sowing of the tempestual Hunger.” কবিতা কোনো নিরপেক্ষতার মাপকাঠি নয়, কবিতা শুধুমাত্র ছন্দ-শব্দ দিয়ে বেঁধে রাখার নান্দনিকতা নয়। বরং, অসহ্য জীবনকে তার মধ্যে প্রতিটি ছত্রে রেখে দেওয়া, অনন্ত বিস্ফারের সম্ভাবনায়। আর, এখানেই মনে পড়ে মারাঠি কবি নামদেও ধাসালের লেখা। দলিত জীবনের আখ্যান এবং প্রতিটি পংক্তিতে উল্লেখযোগ্য ঘৃণা; এই ঘৃণাই আসলে জীবন, এখান থেকে ভালবাসার জন্ম।”
এখানে উল্লেখ্য যে নবারুণ ভট্টাচার্যের বাবা-মা দুজনেই ছিলেন শিক্ষিত এবং উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারের, কলকাতার সংস্কৃতি জগতের মানুষ । অপরপক্ষে হাংরি আন্দোলনের কবি দেবী রায় এসেছিলেন চাষি পরিবার থেকে; এমনকি কলকাতার সাহিত্যিকদের টিটকিরি প্রতিহত করার জন্য তিনি পতৃদত্ত নাম হারাধন ধাড়া বর্জন করতে বাধ্য হন। সুবিমল বসাক এসেছিলেন তাঁতি পরিবার থেকে যাঁর বাবা স্যাকরার কাজ করতে বাধ্য হন এবং মোরারজি দেশাইয়ের গোল্ড কনট্রোলের দরুন দেনার দায়ে আত্মহত্যা করেন । অবনী ধর ছিলেন জাহাজের খালাসি, বাড়ি ফিরে কলকাতার রাস্তায় হকারি করতেন, ঠেলায় করে কয়লা বেচতেন, ফুটপাতে ছিট কাপড় বেচতেন । এই ধরণের জীবনে জড়িয়ে হাংরি-দের লেখায় পরিপার্শ্বের প্রেক্ষিতে আত্ম-কে আবিষ্কার জরুরি হয়ে ওঠে , জীবনের কেন্দ্রের মূল উৎস গুলোয় ফেরা, সন্ধান করা অসুখের উৎসের। কবিতা থেকে কবিতাযাপন হয়ে ওঠার প্রক্রিয়া। ক্রাইসিস-গুলোকে চিনে নিতে নিতে প্রতিস্পর্ধী হয়ে ওঠা। কবিতা মানে বাস্তব থেকে দূরে সরার, অথবা কিছু মিথ্যে স্তোকবাক্য দিয়ে বাস্তবকে আড়াল করার চেষ্টা আর নেই; চাঁদ ফুল তারা নদী আর অতটাও সুন্দর নেই যে তারাই হয়ে উঠতে পারে ‘Aesthetics’-র মাপকাঠি। এস্থেটিক্স-ও নিয়ন্ত্রিত হয় পুঁজির দ্বারা, পুঁজির স্বার্থেই! সেই এস্থেটিক্স কে প্রবল বিক্ষোভে উপহাস করেন ফাল্গুনী রায়ও- “রাজহাঁস ও ফুলবিষয়ক কবিতাগুলি আমি মাংস রাঁধার জন্যেই দিয়েছিলাম উনোনে...”। বরং দৈনন্দিন যুদ্ধদীর্ণ ‘অসুস্থ’ জীবন থেকেই উঠে আসে ‘Aesthetics’-র সারবত্তা। আর, কবির নিশ্চয়ই দায়বদ্ধতা থাকে সমাজের প্রতি; হাংরি-দের সেই নিজেকে, ভাষাকে, কবিতাকে, নাটককে, ছিঁড়েখুঁড়ে সত্যের কাছাকাছি পৌছানোর উপলব্ধিকে ঔপনিষদীয় বলা ভুল হবে না ।
রাষ্ট্রের ভণ্ডামিগুলো, ‘আদার্’ অর্থাৎ’অপর’ ছাপ্পা মেরে দেওয়াগুলো, ‘নিজেকে নিজের মতো গুছিয়ে নেওয়া’র গড্ডালিকা স্রোতগুলোর পালটা স্রোত সাহিত্যে-জীবনযাপনে আসে। আর, যতোটা ‘সংস্কৃতি’ ঠিক করে দেওয়া কর্তারা থাকবে, ততটাই থাকবে সেই ‘সংস্কৃতিকে’ প্রত্যাখ্যান। হয়তো সমান্তরাল, তবু থাকবে। প্রবলভাবেই। সমাজশাসকেরা বরাবরই নিজেদের মত করে হেজিমনি চাপিয়ে দেয়, শাসনের ডিস্কোর্সের অভিমুখে দাঁড় করাতে চায় সব্বাইকে। আর, যখনই তার বিরুদ্ধে স্বর ওঠে, তা সে সাহিত্যেই হোক বা রাজনিতিতে , তাকে দমিয়ে দেওয়া হয়। ব্রাত্য করে রাখা হয় ‘সংস্কৃতি’-র শুদ্ধতার দোহাই দিয়ে। জাতীয় সাহিত্যের মাপকাঠিতে ‘অশ্লীল’ বা ‘রাষ্ট্রদ্রোহী’ হিসেবে প্রতিপন্ন হয় এই সাহিত্যগুলো ও রাজনীতিগুলো । হাংরি আন্দোলনকারীদের যেভাবে জেলে পোরার চক্রান্ত হয়েছিল, একইভাবে প্রতিষ্ঠানের আরও বৃহত্তর চক্রান্তে একের পর এক হত্যা করে নিশ্চিহ্ণ করা হয়েছিল নকশালদের, সমাজকে ‘শুদ্ধ’ করে তোলার জন্য।
অরবিন্দ প্রধান সম্পাদিত ‘অপর : তত্ব ও তথ্য’ বইতে সমীর রায়চৌধুরী লিখেছেন, “নিজেদের রয়ালিস্ট, প্রকৃত খ্রিস্টিয়, প্রগতিবাদী ইত্যাদি নির্দিষ্টাত্মক বিশেষণের খপ্পরের ছাঁচে ফেলে দেওয়ার তোড়জোড়ে সাম্রাজ্যবাদী চেতনার জোয়ারে ভাসিয়ে দিয়েছেন ঔপনিবেশিক শ্রেষ্ঠত্ববোধসম্পন্ন লেখকরা, ফলে তাঁদের টেক্সটে আশ্রিত হয়েছে চরম অপরত্ব-বোধ । দক্ষিণ আফ্রিকার ঔপন্যাসিক জে. এম. কোয়েতসে তাঁর ‘ওয়েটিং ফর দ্য বারবারিয়ানস’ গ্রন্হে দেখিয়েছেন কীভাবে সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য অপরায়নের প্রক্রিয়া কার্যকরী করে । এই প্রক্রিয়া তার নিজের শ্রেষ্ঠত্ব, এগিয়ে থাকা, সভ্যতাকে শ্রেয় এবং অপরের অসত্বিত্বকে হেয় করতে সাহয্য করে । কেবল টেক্সটে নয়, জীবনের সব এলাকাতে এভাবে স্ব-আধিপত্য প্রতিষ্ঠা সহজ হয়ে ওঠে ।” বলা বাহুল্য যে হাংরি আন্দোলন আর নকশাল আন্দোলনকে পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসন ‘অপর’ তকমা দিয়ে সমাজ থেকে মুছে ফেলতে চেয়েছিল, যেমন আফ্রিকার আদিনিবাসদের মুছে ফেলতে চেয়েছিল ইউরোপের শাসক-সমাজ ।
নারায়ণ সান্যালের বিবরণীতে বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙার এক অজানা কথা উঠে আসে। “কলেজ স্কোয়ারে বিদ্যাসাগর-মশায়ের মর্মরমূর্তির যেদিন মুণ্ডচ্ছেদ হয় তার মাসখানেকের মধ্যে সিপিএম (এম. এল) দলের এক নেতৃত্বস্থানীয় ছাত্রনেতার সঙ্গে আমার সাক্ষাত্ হয়েছিল! ঘটনাচক্রে সে আমার নিকট আত্মীয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। কট্টর নকশাল। আমার পেচকপ্রতিম বিরস মুখখানা দেখে সে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিল, ‘বিশ্বাস কর ছোটকাকু! মূর্তিটা যে ভেঙ্গেছে তাকে আমি চিনি। গত বছর হায়ার সেকেন্ডারিতে সে বাংলায় লেটার পেয়েছে। ওর সেই বাংলা প্রশ্নপত্রে প্রবন্ধ এসেছিল তোমার প্রিয় দেশবরেণ্য নেতা। ও লিখেছিল বিদ্যাসাগরের উপর।”
অধিকাংশ আলোচক বলেন হাংরি আন্দোলন এবং নকশাল আন্দোলন দুটিই ব্যর্থ্য এবং তাদের ব্যর্থতার কারণও এক : প্রথমত, প্রশাসনিক আক্রমণ ; দ্বিতীয়ত, আন্দোলনের নেতাদের মধ্যে মতবিরোধ ; তৃতীয়ত, আন্দোনের সদস্যদের মধ্যে বিভাজন ; চতুর্থত, তাঁদের কার্যকলাপ । আমি শুধু বলতে চাই যে দুটি আন্দোলনই বাংলার বৌদ্ধিক সমাজে ছাপ ফেলেছে এবং তা ‘ব্যর্থ্য’ তকমা দিয়ে চাপা দেয়া যায় না ।
পাঁচ
হাংরি আন্দোলনকারীদের মত পরাবাস্তব আন্দোলনকারীদের মাঝেও ভাঙন ঘটত, সে কথাও জানিয়েছেন অভিজিৎ পাল ।
১৯১৭ সালে গিয়ম অ্যাপলিনেয়ার “সুররিয়ালিজম” অভিধাটি তৈরি করেছিলেন, যার অর্থ ছিল বাস্তবের অতীত। শব্দটি প্রায় লুফে নেন আঁদ্রে ব্রেতঁ, নতুন একটি আন্দোলন আরম্ভ করার পরিকল্পনা নিয়ে, যে আন্দোলনটি হবে পূর্ববর্তী ডাডাবাদী আন্দোলন থেকে ভিন্ন । ত্রিস্তঁ জারা উদ্ভাবিত ডাডা আন্দোলন থেকে সরে আসার কারণ হল ব্রেতঁ সহ্য করতে পারতেন না ত্রিস্তঁ জারাকে, কেননা কবি-শিল্পী মহলে প্রতিশীল্পের জনক হিসাবে ত্রিস্তঁ জারা খ্যাতি পাচ্ছিলেন। আঁদ্রে ব্রেতঁ সুররিয়ালিজম তত্বটির একমাত্র ব্যাখ্যাকারী হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে আরম্ভ করেন। ১৯১৯ সালে ত্রিস্তঁ জারাকে কিন্তু ব্রেতঁ চিঠি লিখে প্যারিসে আসতে বলেছিলেন । একইভাবে ‘হাংরি’ শব্দটি মলয় রায়চৌধুরী পেয়েছিলেন কবি জিওফ্রে চসার থেকে । এই ‘হাংরি’ শব্দটি নেয়ার জন্য মলয় রায়চৌধুরীকে যেভাবে আক্রমণ করা হয়েছে, তেমন কিছুই করা হয়নি আঁদ্রে ব্রেতঁ ও ত্রিস্তঁ জারা সম্পর্কে । মলয় রায়চৌধুরী হাংরি জেনারেশন আন্দোলন ঘোষণা করেন ১৯৬৫ সালের পয়লা নভেম্বর একটি লিফলেট প্রকাশের মাধ্যমে ।
পরাবাস্তববাদী আন্দোলনে, প্রথম থেকেই, আঁদ্রে ব্রেতঁ’র সঙ্গে অনেক পরাবাস্তববাদীর সদ্ভাব ছিল না, কিন্তু পরাবাস্তববাদ বিশ্লেষণের সময়ে আলোচকরা তাকে বিশেষ গুরুত্ব দেন না । আমরা যদি বাঙালি আলোচকদের কথা চিন্তা করি, তাহলে দেখব যে তাঁরা হাংরি জেনারেশন বা ক্ষুধার্ত আন্দোলন বিশ্লেষণ করার সময়ে হাংরি জেনারেশনের সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে অত্যধিক চিন্তিত, হাংরি আন্দোলনকারীদের সাহিত্য অবদান নিয়ে নয় । ব্যাপারটা বিস্ময়কর নয় । তার কারণ অধিকাংশ আলোচক হাংরি জেনারেশনের সদস্যদের বইপত্র সহজে সংগ্রহ করতে পারেন না এবং দ্বিতীয়ত সাংবাদিক-আলোচকদের কুৎসাবিলাসী প্রবণতা ।
আঁদ্রে ব্রেতঁ তাঁর বন্ধু পল এলুয়ার, বেনিয়ামিন পেরে, মান রে, জাক বারোঁ, রেনে ক্রেভালl, রোবের দেসনস, গিয়র্গে লিমবোর, রোজের ভিত্রাক, জোসেফ দেলতিল, লুই আরাগঁ ও ফিলিপে সুপোকে নিয়ে ১৯১৯ পরাবাস্তববাদ আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন । কিছুকাল পরে, রাজনৈতিক ভাবাদর্শের কারণে তাঁর সঙ্গে লুই আরাগঁর ঝগড়া বেধে গিয়েছিল । মার্সেল দ্যুশঁ, ত্রিস্তঁ জারা এবং আঁদ্রে ব্রেতঁ, উভয়ের সঙ্গেই ছিলেন, এবং দুটি দলই তাঁকে গুরুত্ব দিতেন, দ্যুশঁ’র অবাস্তব ও অচিন্ত্যনীয় ভাবনার দরুন।
পরাবাস্তব আন্দোলনের আগে জুরিখে ডাডাবাদী আন্দোলন আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল এবং আঁদ্রে ব্রেতঁ পরাবাস্তববাদের অনুপ্রেরণা পান ডাডা আন্দোলনের পুরোধা ত্রিস্তঁ জারার কাছ থেকে, কিন্তু ব্রেতঁ চিরকাল তা অস্বীকার করে্ছেন । ডাডা ছিল শিল্পবিরোধী আভাঁ গার্দ আন্দোলন ; অবশ্য প্রতিশিল্পও তো শিল্প । ডাডাবাদের রমরমার কারণে ত্রিস্তঁ জারার সঙ্গে ব্রেতঁর সম্পর্ক দূষিত হয়ে যায় ; একজন অন্যজনের নেতৃত্ব স্বীকার করতে চাইতেন না । ডাডা (/ˈdɑːdɑː/) বা ডাডাবাদ (দাদাবাদ নামেও পরিচিত) ছিল ২০ শতকের ইউরোপীয় ভিন্নচিন্তকদের একটি সাহিত্য-শিল্প আন্দোলন, যার প্রাথমিক কেন্দ্র ছিল সুইজারল্যান্ডের জুরিখে ক্যাবারে ভলতেয়ার ( ১৯১৬ নাগাদ ) এবং নিউ ইয়র্কে (প্রায় ১৯১৫ নাগাদ)। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় ডাডা আন্দোলন গড়ে ওঠে সেইসব শিল্পীদের নিয়ে, যাঁরা পুঁজিবাদী সমাজের যুক্তি, কারণ বা সৌন্দর্যের ধারণা মানতেন না, বরং তাঁদের কাজের মাধ্যমে প্রকাশ করতেন আপাত-অর্থহীন, উদ্ভট, অযৌক্তিক এবং বুর্জোয়া-বিরোধী প্রতিবাদী বক্তব্য । আন্দোলনটির শিল্পচর্চা প্রসারিত হয়েছিল দৃশ্যমান, সাহিত্য ও শব্দ মাধ্যমে, যেমন- কোলাজ, শব্দসঙ্গীত, কাট-আপ লেখা, এবং ভাস্কর্য। ডাডাবাদী শিল্পীরা হানাহানি, যুদ্ধ এবং জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে অসন্তোষ প্রকাশ করতেন এবং গোঁড়া বামপন্থীদের সাথে তাঁদের রাজনৈতিক যোগাযোগ ছিল।
যুদ্ধ-পূর্ববর্তী প্রগতিবাদীদের মধ্যেই ডাডার শিকড় লুকিয়ে ছিল। শিল্পের সংজ্ঞায় পড়েনা এমন সব সৃষ্টিকর্মকে চিহ্নিত করার জন্য ১৯১৩ সালে "প্রতি-শিল্প" শব্দটি চালু করেছিলেন মার্সেল দ্যুশঁ । কিউবিজম এবং কোলাজ ও বিমূর্ত শিল্পের অগ্রগতিই হয়তো ডাডা আন্দোলনকে বাস্তবতার গন্ডী থেকে বিচ্যুত হতে উদ্বুদ্ধ করে। আর শব্দ ও অর্থের প্রথানুগত সম্পর্ক প্রত্যাখ্যান করতে ডাডাকে প্রভাবিত করে ইতালীয় ভবিষ্যতবাদী এবং জার্মান এক্সপ্রেশনিস্টগণ । আলফ্রেড জ্যারির উবু রোই (১৮৯৬) এবং এরিক স্যাটির প্যারেড (১৯১৬-১৭) প্রভৃতি লেখাগুলোকে ডাডাবাদী রচনার আদিরূপ বলা যেতে পারে। ডাডা আন্দোলনের মূলনীতিগুলো প্রথম সংকলিত হয় ১৯১৬ সালে হুগো বলের ডাডা ম্যানিফেস্টোতে। এই ম্যানিফেস্টোর প্রভাবে পরবর্তিকালে ব্রেতঁ সুররিয়ালিস্ট ম্যানিফেস্টো লিখতে অনুপপ্রাণিত হন -- এই কথা শুনতে ব্রেতঁ’র ভালো লাগত না এবং সেকারণে তিনি বহু সঙ্গীকে এক-এক করে আন্দোলন থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন । তাছাড়া ব্রেতঁ মনে করতেন ডাডাবাদীরা নৈরাজ্যবাদী বা অ্যানার্কিস্ট, যখন কিনা তিনি একজন কমিউনিস্ট ।
ডাডা আন্দোলনে ছিল জনসমাবেশ, মিছিল ও সাহিত্য সাময়িকীর প্রকাশনা; বিভিন্ন মাধ্যমে শিল্প, রাজনীতি এবং সংস্কৃতি নিয়ে তুমুল আলোচনা হতো। আন্দোলনের প্রধান ব্যক্তিত্বরা ছিলেন হুগো বল, মার্সেল দ্যুশঁ, এমি হেনিংস, হানস আর্প, রাউল হাউসম্যান, হানা হৌক, জোহান বাডার, ত্রিস্তঁ জারা, ফ্রান্সিস পিকাবিয়া, রিচার্ড হিউলসেনব্যাক, জর্জ গ্রোস, জন হার্টফিল্ড, ম্যান রে, বিয়াট্রিস উড, কার্ট শ্যুইটার্স, হানস রিখটার এবং ম্যাক্স আর্নেস্ট। অন্যান্য আন্দোলন, শহরতলীর গান এসবের পাশাপাশি পরাবাস্তববাদ, নব্য বাস্তবতা, পপ শিল্প এবং ফ্লক্সেস প্রভৃতি গোষ্ঠীগুলোও ডাডা আন্দোলন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। এই আন্দোলনের অনেকে সুররিয়ালিস্ট আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন ।
পরাবাস্তববাদ আন্দোলনে যাঁরা ব্রেতঁর সঙ্গে একে-একে যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের অন্যতম হলেন ফিলিপে সুপো, লুই আরাগঁ, পল এলুয়ার, রেনে ক্রেভাল, মিশেল লেইরিস, বেনিয়ামিন পেরে, অন্তনাঁ আতো,জাক রিগো, রবের দেসনস, ম্যাক্স আর্নস্ত প্রমুখ । এঁদের অনেকে ডাডাবাদী আন্দোলন ত্যাগ করে পরাবাস্তববাদী আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯২৩ সালে যোগ দেন চিত্রকর আঁদ্রে মাসোঁ ও ইভস তাঙ্গুই । ১৯২১ সালে ভিয়েনায় গিয়ে ফ্রয়েডের সঙ্গে দেখা করেন ব্রেতঁ । ফ্রয়েডের ধারণাকে তিনি সাহিত্য ও ছবি আঁকায় নিয়ে আসতে চান । ফ্রয়েডের প্রভাবে ব্রেতঁ বললেন, সুররিয়ালিজমের মূলকথা হল অবচেতনমনের ক্রিয়াকলাপকে উদ্ভট ও আশ্চর্যকর সব রূপকল্প দ্বারা প্রকাশ করা। ডাডাবাদীরা যেখানে চেয়েছিলেন প্রচলিত সামাজিক মূল্যবোধকে নস্যাৎ করে মানুষকে এমন একটি নান্দনিক দৃষ্টির অধিকারী করতে যার মাধ্যমে সে ভেদ করতে পারবে ভণ্ডামি ও রীতিনীতির বেড়াজাল, পৌঁছাতে পারবে বস্তুর অন্তর্নিহিত সত্যে; সেখানে পরাবাস্তববাদ আরো একধাপ এগিয়ে বলল, প্রকৃত সত্য কেবলমাত্র অবচেতনেই বিরাজ করে। পরাবাস্তববাদী শিল্পীর লক্ষ্য হল তার কৌশলের মাধ্যমে সেই সত্যকে ব্যক্তি-অস্তিত্বের গভীর থেকে তুলে আনা।
সুররিয়ালিজমের প্রথম ইশতেহার প্রকাশ করেন ইয়ান গল। এ ইশতেহারটি ১৯২৪ সালের ১ অক্টোবর প্রকাশিত হয়। এর কিছুদিন পরেই ১৫ অক্টোবর আঁদ্রে ব্রেতঁ সুররিয়ালিজমের দ্বিতীয় ইশতেহারটি প্রকাশ করেন। তিনি ১৯৩০ সালে এ ধারার তৃতীয় ইশতেহারটিও প্রকাশ করেন। ইয়ান গল ও আঁদ্রে ব্রেতঁ—দুজনে দু দল সুররিয়ালিস্ট শিল্পীর নেতৃত্ব দিতেন। ইয়ান গলের নেতৃত্বে ছিলেন ফ্রান্সিস পিকাবিয়া, ত্রিস্তঁ জারা, মার্সেল আর্লেন্ড, জোসেফ ডেলটিল, পিয়েরে অ্যালবার্ট বিরোট প্রমুখ। আন্দ্রে ব্রেতঁর নেতৃত্বে ছিলেন লুই আরাগঁ, পল এলুয়ায়, রোবের ডেসনোস, জ্যাক বারোঁ, জর্জ ম্যালকিন প্রমুখ। এ দুটি দলেই ডাডাইজম আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ ছিলেন। অবশ্য ইয়ান গল ও আন্দ্রে ব্রেতঁ এই আন্দোলন নিয়ে প্রকাশ্য-রেশারেশিতে জড়িয়ে পড়েন। তখন থেকেই পরাবাস্তববাদীরা ছোটো-ছোটো গোষ্ঠীতে বিভাজিত হতে থাকেন, যদিও তাঁদের শিল্প ও সাহিত্যধারা ছিল একই । পরে আন্দোলনে যোগ দেন জোয়ান মিরো, রেমণ্ড কোয়েনু, ম্যাক্স মোরিজ, পিয়ের নাভিল, জাক আঁদ্রে বোইফার, গেয়র্গে মালকাইন প্রমুখ । জিয়োর্জিও দে চিরোকো এবং পাবলো পিকাসো অনেক সময়ে গোষ্ঠির কর্মকাণ্ডে অংশ নিতেন, তবে আন্দোলনের ঘোষিত সদস্য ছিলেন না।
সুররিয়ালিজম বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য ডাডাইজম থেকে নিলেও এই মতবাদটি, যে, ‘শিল্পের উৎস ও উপকরণ’ বিবেচনায় একটি অন্যটির চেয়ে স্বতন্ত্র্য। সুররিয়ালিজম আন্দোলনের সামনের সারিতে ছিলেন ফরাসি কবি আঁদ্রে ব্রেতঁ। তিনি শিল্প রচনায় ‘অচেতন মনের ওপর গুরুত্ব’ দেওয়ার জন্যে শিল্পীদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি মনে করতেন, ‘অচেতন মন হতে পারে কল্পনার অশেষ উৎস।’ তিনি অচেতন মনের ধারণাটি নিঃসন্দেহে সিগমুন্ড ফ্রয়েডের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। ডাডাবাদী শিল্পীরা শিল্পের উৎস ও উপকরণ আহরণে ‘অচেতন’ মনের ধারণা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না। সুররিয়ালিস্ট শিল্পীরা এসে অচেতন মনের উৎস থেকে শিল্প রচনার প্রতি গুরুত্ব দেন এবং সফলতাও লাভ করেন।
আঁদ্রে ব্রেতঁ মনে করতেন, ‘যা বিস্ময়কর, তা সবসময়ই সুন্দর’। অচেতন মনের গহীনেই বিস্ময়কর সুন্দরের বসবাস। তার সন্ধান করাই সাহিত্যিক-শিল্পীর যথার্থ কাজ। অচেতন মনের কারণেই সুররিয়ালিজমের কবি-শিল্পীরা গভীর আত্মঅনুসন্ধানে নামেন। মনের গহীন থেকে স্বপ্নময় দৃশ্যগুলো হাতড়ে বের করতে এবং মনের অন্তর্গত সত্য উন্মোচনে তাঁরা আগ্রহী ছিলেন। যার কারণে চেতন ও অচেতনের মধ্যে শিল্পীরা বন্ধন স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সুররিয়ালিস্ট শিল্পীরা অচেতন মনের সেই সব উপলব্ধিকে দৃশ্যে রূপ দিলেন যা পূর্বে কেউ কখনো করেনি। অচেতনের ভূমিতে দাঁড়িয়ে বাস্তব উপস্থাপনের কারণে খুব দ্রুতই এ মতবাদটি বিশ্ব শিল্পকলায় ‘অভিনবত্ব’ যোগ করতে সমর্থ হয়। এমনকী, পুঁজিবাদ-বিরোধী এই আন্দোলন থেকে উপকরণ সংগ্রহ করেছেন বহু বিখ্যাত বিজ্ঞাপন কোম্পানি ।
সুররিয়ালিজমকে ‘নির্দিষ্ট’ ছকে ফেলা কঠিন। সুররিয়ালিস্ট শিল্পীরা একই ছাতার নিচে বসবাস করে ছবি আঁকলেও এবং কবিতা লিখলেও, তাঁদের দৃষ্টি ও উপলব্ধির মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। ফলে এ মতবাদটি সম্পর্কে প্রত্যেকে ব্যাক্তিগত ভাবনা ভেবেছেন। ১৯২৯ সালে সালভাদর দালি এই আন্দোলনে যোগ দেন, যদিও তাঁর সঙ্গেও ব্রেতঁর বনিবনা হতো না । সালভাদর দালি মনে করতেন, ‘সুররিয়ালিজম একটি ধ্বংসাত্মক দর্শন এবং এটি কেবল তা-ই ধ্বংস করে যা দৃষ্টিকে সীমাবদ্ধ রাখে।’ অন্যদিকে জন লেলন বলেছেন, ‘সুররিয়ালিজম আমার কাছে বিশেষ প্রভাব নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। কেননা, আমি উপলব্ধি করেছিলাম আমার কল্পনা উন্মাদনা নয়। বরং সুররিয়ালিজমই আমার বাস্তবতা।’ ব্রেতোঁ বলতেন, ‘ভাবনার যথাযথ পদ্ধতি অনুধাবনের জন্যে সুররিয়ালিজম আবশ্যক।’ এ ধারায় স্বপ্ন ও বাস্তবতার মিশ্রণ হয় বলে সুররিয়ালিজমকে স্বপ্নবাস্তবতাও বলা হয়ে থাকে।
সুররিয়ালিজমের ঢেউ খুব অল্প সময়েই শিল্পের সবগুলো শাখায় আছড়ে পড়ে। কবিতা, গান থেকে শুরু করে নাটক, সিনেমা পর্যন্ত সুররিয়ালিস্টদের চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। ১৯২৪ সাল থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত সুররিয়ালিজম ধারায় অন্তত ছয়টি সিনেমা নির্মিত হয়। এ ধারার প্রধান শিল্পীরা হলেন জ্যাঁ আর্প, ম্যাক্স আর্নেস্ট, আঁদ্রে মেসন, সালভাদর দালি, রেনে ম্যাগরেট, পিয়েরো রয়, জোয়ান মিরো, পল ডেলভাক্স, ফ্রিদা কাহলো প্রমুখ। এ ধারার চিত্রকর্মের মধ্যে ১৯৩১ সালে আঁকা সালভাদর দালির ‘দ্য পারসিসটেন্স অব মেমোরি’ সবচেয়ে আলোচিত ছবি। এটি কেবল এ ধারার মধ্যেই আলোচিত চিত্রকর্মই নয়, এটি দালিরও অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিভার নিদর্শন। ‘দ্য পারসিসটেন্স অব মেমোরি’-তে দালি ‘সময়ের’ বিচিত্র অবস্থাকে ফ্রেমবন্দি করতে চেষ্টা করেছেন। ‘মেটামরফসিস অব নার্সিসাস’, ‘নভিলিটি অব টাইম’, ‘প্রোফাইল অব টাইম’ প্রভৃতি তাঁর গুরুত্বপূর্ণ কাজ।
সুররিয়ালিজম ধারার প্রধানতম চিত্রকর্মের মধ্যে রেনে ম্যাগরেটের ‘দ্য সন অব ম্যান’, ‘দিস ইজ নট এ পাইপ’, জর্জিও দি চিরিকো-এর ‘দ্য রেড টাওয়ার’, ম্যাক্স আর্নেস্টের ‘দি এলিফ্যান্ট সিলিবেস’, ইভ তঁগির ‘রিপ্লাই টু রেড’ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে সুররিয়ালিজম আন্দোলন থেমে যায়। শিল্পবোদ্ধারা মনে করেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষের মধ্য দিয়ে এ আন্দোলনটির অনানুষ্ঠানিক মৃত্যু ঘটে। কিন্তু অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আন্দোলনের মতো সুররিয়ালিজমের চর্চা বর্তমানেও হচ্ছে। বাংলাদেশের শিল্পাঙ্গনেও সুররিয়ালিজমের প্রভাব লক্ষ করা যায়। ১৯২৪ সালে প্রকাশ করেন তাঁর প্রথম সুররিয়ালিস্ট ম্যানিফেস্টো । মার্কসবাদের সঙ্গে আর্তুর র্যাঁবোর আত্মপরিবর্তনের ভাবনাকে একত্রিত করার উদ্দেশে ব্রেতঁ ১৯২৭ সালে ফরাসি কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন । কিন্তু সাম্যবাদীদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বেশিদিন টেকেনি । সেখান থেকেও তিনি ১৯৩৩ সালে বিতাড়িত হন । পরাবাস্তববাদীদের “উন্মাদ প্রেম” তত্বটি ব্রেতঁর এবং “উন্মাদ প্রেম” করার জন্য বেশ কিছু তরুণী সুররিয়ালিস্টদের প্রতি আকৃষ্ট হন । যৌনতার স্বেচ্ছাচারিতার ঢেউ ওঠে সাহিত্যিক ও শিল্পী মহলে ; পরাবাস্তববাদীদের নামের সঙ্গে একজন বা বেশি নারীর সম্পর্ক ঘটে এবং সেই নারীরা তাঁদের পুরুষ প্রেমিকদের নামেই খ্যাতি পেয়েছেন ।
তাঁর রাজনৈতিক টানাপোড়েন এবং অন্যান্য কারণে প্রেভের, বারোঁ, দেসনস, লেইরিস, লিমবোর, মাসোঁ, কোয়েন্যু, মোরিস, বোইফার সম্পর্কচ্ছদ করেন ব্রেতঁর সঙ্গে এবং গেয়র্গে বাতাইয়ের নেতৃত্বে পৃথক গোষ্ঠী তৈরি করেন । এই সময়েই, ১৯২৯ নাগাদ, ব্রেতঁর গোষ্ঠীতে যোগ দেন সালভাদর দালি, লুই বুনুয়েল, আলবের্তো জিয়াকোমেত্তি, রেনে শার এবং লি মিলার । ত্রিস্তঁ জারার সঙ্গে ঝগড়া মিটমাট করে নেন ব্রেতঁ । দ্বিতীয় সুররিয়ালিস্ট ইশতাহার প্রকাশের সময়ে তাতে সই করেছিলেন আরাগঁ, আর্নস্ট, বুনুয়েল, শার, ক্রেভাল, দালি, এলুয়ার, পেরে, টাঙ্গুই, জারা, ম্যাক্সিম আলেকজান্দ্রে, জো বনসকোয়েত, কামিলে গোয়েমানস, পল নুগ, ফ্রান্সিস পোঙ্গে, মার্কো রিসটিচ, জর্জ শাদুল, আঁদ্রে তিরিয়ঁ এবং আলবেয়ার ভালেনতিন । ফেদেরিকো গারথিয়া লোরকা বন্ধু ছিলেন সালভাদর দালি এবং লুই বুনুয়েলের, আলোচনায় অংশ নিতেন, কিন্তু সুররিয়ালিস্ট গোষ্ঠিতে যোগ দেননি । ১৯২৯ সালে তাঁর মনে হয়েছিল যে দালি আর বুনুয়েলের ফিল্ম “একটি আন্দালুসিয় কুকুর” তাঁকে আক্রমণ করার জন্যে তৈরি হয়েছিল ; সেই থেকে তিনি সুররিয়ালিস্টদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন । আরাগঁ ও জর্জ শাদুল ব্রেতঁ’র গোষ্ঠী ত্যাগ করেছিলেন রাজনৈতিক মতভেদের কারণে, যদিও ব্রেতঁ বলতেন যে তিনিই ওনাদের তাড়িয়েছেন ।
১৯৩০ সালে কয়েকজন পরাবাস্তববাদী আঁদ্রে ব্রেতঁ’র একচেটিয়া নেতৃত্বে বিরক্ত হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে একটি প্যামফ্লেট ছাপিয়েছিলেন । পরাবাস্তববাদ আন্দোলন দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় । ১৯৩৫ সালে ব্রেতঁ এবং সোভিয়েত লেখক ও সাংবাদিক ইলিয়া এরেনবার্গের মাঝে ঝগড়া এমন স্তরে গিয়ে পৌঁছোয় যে প্যারিসের রাস্তায় তাঁদের দুজনের হাতাহাতি আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল । এরেনবার্গ একটি পুস্তিকা ছাপিয়ে বলেছিলেন যে পরাবাস্তববাদীরা পায়ুকামী । এর ফলে পরাবাস্তববাদীদের ইনটারন্যাশানাল কংগ্রেস ফর দি ডেফেন্স অফ কালচার সংস্হা থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল । সালভাদর দালি বলেছিলেন যে পরাবাস্তববাদীদের মধ্যে প্রকৃত সাম্যবাদী হলেন একমাত্র রেনে ক্রেভাল । চটে গিয়ে ক্রেভালকে পরাবাস্তববাদী আন্দোলন থেকে বের করে দ্যান ব্রেতঁ । অঁতনা অতো, ভিত্রাক এবং সুপোকে পরাবাস্তববাদী দল থেকে বের করে দ্যান ব্রেতঁ, মূলত সাম্যবাদের প্রতি ব্রেতঁর আত্মসমর্পণের কারণে এই তিনজন বিরক্ত বোধ করেন ।
১৯৩৮ সালে ব্রেতঁ মেকসিকো যাবার সুযোগ পান এবং লিও ট্রটস্কির সঙ্গে দেখা করেন । তাঁর সঙ্গে ছিলেন দিয়েগো রিভেরা ও ফ্রিদা কালহো । ট্রটস্কি এবং ব্রেতঁ একটা যুক্ত ইশতাহার প্রকাশ করেছিলেন, “শিল্পের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা” শিরোনামে । লুই আরাগঁর সঙ্গেও ব্রেতঁর সম্পর্ক ভালো ছিল না । ১৯১৯ থেকে ১৯২৪ পর্যন্ত ডাডাবাদীদের সঙ্গে আন্দোলন করার পর ১৯২৪ সালে আরাগঁ যোগ দেন পরাবাস্তববাদী আন্দোলনে । অন্যান্য ফরাসী পরাবাস্তববাদীদের সঙ্গে তিনিও ফরাসি কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দ্যান এবং পার্টির পত্রিকায় কলাম ও রাজনৈতিক কবিতা লিখতেন । আরাগঁর সঙ্গে ব্রেতঁর বিবাদের কারণ হল ব্রেতঁ চেয়েছিলেন ট্রটস্কির সঙ্গী ভিকতর সার্জকে সন্মানিত করতে । পরবর্তীকালে, ১৯৫৬ নাগাদ, সোভিয়েত রাষ্ট্র সম্পর্কে নিরাশ হন আরাগঁ, বিশেষ করে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির বিংশ কংগ্রেসের পর যখন নিকিতা ক্রুশ্চভ আক্রমণ করেন জোসেফ স্তালিনের ব্যক্তিত্ববাদকে । তা সত্ত্বেও স্তালিনপন্হী আরাগঁ ও ট্রটস্কিপন্হী ব্রেতঁর কখনও মিটমাট হয়নি । কাট-আপ কবিতার জনক ব্রায়ন জিসিনকেও গোষ্ঠী থেকে বিতাড়ন করেন ব্রেতঁ ; ব্রায়ান জিসিনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ছিলেন বিট ঔপন্যাসিক উইলিয়াম বারোজ । বিট আন্দোলনের প্রায় সকলেই সুররিয়ালিজম দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন । বিটদের যৌন স্বাধীনতার ভাবনা-চিন্তায় সুররিয়ালিস্টদের অবদান আছে ।
পরাবাস্তববাদই সম্ভবত প্রথম কোনো গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন, যেখানে নারীকে দূরতম কোনো নক্ষত্রের আলোর মতো, প্রেরণা ও পরিত্রাণের মতো, কল্পনার দেবী প্রতিমার মতো পবিত্র এক অবস্থান দেওয়া হয়েছিল। নারী তাদের চোখে একই সঙ্গে পবিত্র কুমারী, দেবদূত আবার একই সঙ্গে মোহিনী জাদুকরী, ইন্দ্রিয় উদ্দীপক ও নিয়তির মতো অপ্রতিরোধ্য। ১৯২৯ সালে দ্বিতীয় সুররিয়ালিস্ট ম্যানিফেস্টোয় আদ্রেঁ ব্রেতঁ নারীকে এরকম একটি অপার্থিব অসীম স্বপ্নিল চোখে দেখা ও দেখানোর চেষ্টা করেছিলেন। পুরুষ শিল্পীদের প্রেরণা, উদ্দীপনা ও কল্পনার সুদীর্ঘ সাম্পান হয়ে এগিয়ে আসবেন নারীরা। হয়ে উঠবেন পুরুষদের আরাধ্য ‘মিউজ’ আর একই সঙ্গে femme fatale। সুদৃশ্য উঁচু পূজার বেদি উদ্ভাসিত করে যেখানে বসে থাকবেন নারীরা। তাঁদের স্বর্গীয় প্রাসাদে আরো সৃষ্টিশীল হয়ে উঠবে পুরুষ।
ব্রেতঁ ছিলেন সেই সময়ের কবিতার অন্যতম প্রধান পুরুষ। তাঁর সম্মোহক ব্যক্তিত্বে আচ্ছন্ন হননি তাঁর সান্নিধ্যে এসেও – এরকম কোনো দৃষ্টান্ত কোথাও নেই। উজ্জ্বল, সাবলীল, মেধাবী, স্বতঃস্ফূর্ত এবং নায়কসুলভ ব্রেতঁ একই সঙ্গে ছিলেন উদ্ধত, আক্রমণাত্মক ও অহমিকাপূর্ণ। নিজের তাত্ত্বিক অবস্থান থেকে মাঝেমধ্যেই ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে যেতেন। কিন্তু যদি তাঁর একবার মনে হতো যে কেউ তাঁর প্রভুত্বকে অগ্রাহ্য করছে, সর্বশক্তি দিয়ে তাকে আঘাত করতেন। নেতৃত্ব দেওয়ার সব গুণ প্রকৃতিগতভাবেই ছিল তাঁর মধ্যে। মহিলাদের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার ছিল তরুণ প্রেমিকের মতো সম্ভ্রমপূর্ণ। তাঁর আকর্ষণীয় বাচনভঙ্গি, অভিজাত ভাষা – এসবের সঙ্গে মাঝেমধ্যেই মেজাজ হারিয়ে সম্পূর্ণ লাগামহীন হয়ে পড়া আর দুর্বোধ্য জটিল মানসিকতার জন্য পারতপক্ষে অনেকেই ঘাঁটাতে চাইতেন না তাঁকে।
নারী পরাবাস্তববাদীদের সংখ্যা কম ছিল না । কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে উল্লেখ্য ফ্রিদা কাহলো, আসে বার্গ, লিজে দেহামে, আইরিন হামোয়ের, জয়েস মানসোর, ওলগা ওরোজকো, আলেহান্দ্রা পিৎসারনিক, ভ্যালেনটিন পেনরোজ, জিসেল প্রাসিনস, ব্লাঙ্কা ভারেলা, ইউনিকা জুর্ন প্রমুখ । নারী চিত্রকররা সংখ্যায় ছিলেন বেশি । তাঁদের মধ্যে উল্লেখ্য গেরট্রুড আবেরকমবি, মারিয়ন আদনামস, আইলিন ফরেসটার আগার, রাশেল বায়েস, ফ্যানি ব্রেনান, এমি ব্রিজওয়াটার, লেনোরা ক্যারিংটন, ইথেল কলকুহুন, লেনোর ফিনি, জেন গ্রাভেরোল, ভ্যালেনটিন য়োগো, ফ্রিদা খাহলো, রিটা কার্ন-লারসেন, গ্রেটা নুটসন ( ত্রিস্তঁ জারার স্ত্রী ), জাকেলিন লামবা ( আঁদ্রে ব্রেতঁ’র স্ত্রী), মারুহা মালো, মার্গারেট মডলিন, গ্রেস পেইলথর্প, অ্যালিস রাহোন, এডিথ রিমিঙটন, পেনিলোপি রোজমন্ট, কে সেজ ( ইভস তাঙ্গুইর স্ত্রী ), ইভা স্বাঙ্কমাজেরোভা, ডরোথি ট্যানিঙ ( ম্যাক্স আর্নস্টের স্ত্রী ), রেমেদিওস ভারো ( বেনিয়ামিন পেরের স্ত্রী ) প্রমুখ । ভাস্করদের মধ্যে উল্লেখ্য এলিজা ব্রেতঁ ( আঁদ্রে ব্রেতঁ’র তৃতীয় স্ত্রী ), মেরে ওপেনহাইম ( মান রে’র মডেল ছিলেন ) এবং মিমি পারেন্ট । ফোটোগ্রাফারদের মধ্যে উল্লেখ্য ছিলেন ক্লদ কাহুন, নুশ এলুয়ার, হেনরিয়েতা গ্রিনদাত, আইডা কার, দোরা মার ( পাবলো পিকাসোর সঙ্গে নয় বছর লিভ টুগেদার করেছিলেন ), এমিলা মেদকোভা, লি মিলার, কাতি হোরনা প্রমুখ । পুরুষ পরাবাস্তববাদীদের বহু ফোটো এই নারী ফোটোগ্রাফারদের কারণেই ইতিহাসে স্হান পেয়েছে ।
নারীদের নিয়ে পরাবাস্তববাদীদের এই স্বপ্নিল কাব্যময় উচ্ছ্বাস জোরালো একটা ধাক্কা খেল যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পশ্চিম ইউরোপে দ্রম্নত বদলাতে থাকা পরিস্থিতির ভস্ম ও শোণিত স্নাত শোণিত আত্মশক্তিসম্পন্ন নারীরা তাঁদের ভারী বাস্তবতা নিয়ে এসে দাঁড়ালেন সামনে। স্বপ্নে দেখা নারীর আয়না-শরীর ভেঙে পড়ল ঝুরঝুর করে আর বেরিয়ে এলো মেরুদ-সম্পন্ন রক্তমাংসের মানবী। সুররিয়ালিজম চেয়েছিল পুরুষের নিয়ন্ত্রণে নারীদের মুক্তি। কিন্তু যে গভীর অতলশায়ী মুক্তি দরজা খুলে দিলো নারীদের জন্য, সুররিয়ালিজম তার জন্য তৈরি ছিল না। মৃত অ্যালবাট্রসের মতো এই বিমূর্ত আদর্শায়িত ধারণা নারী শিল্পীদের গলায় ঝুলে থেকেছে, যাকে ঝেড়ে ফেলে নিজস্ব শিল্পসত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করা দুঃসাধ্য ছিল। সময় লেগেছে সাফল্য পেতে। কিন্তু দিনের শেষে হেসেছিলেন তাঁরাই। এমন নয় যে, পরাবাস্তবতার প্রধান মশালবাহক ব্রেতঁ চাইছিলেন যে পুরুষরাই হবেন এই আন্দোলনের ঋত্বিক আর দ্যুতিময় নারী শিল্পী এবং সাহিত্যিকদের কাজ হবে মুগ্ধ সাদা পালক ঘাসের ওপরে ফেলে যাওয়া এবং আকর্ষণীয় ‘গুজব’ হিসেবে সুখী থাকা। ১৯২৯ সালে দ্বিতীয় সুররিয়ালিস্ট ম্যানিফেস্টো প্রকাশের পরবর্তী প্রদর্শনীগুলোতে নারী শিল্পীরা সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন ঠিকই। কিন্তু পুরুষ উদ্ভাবিত পরাবাস্তবতা থেকে তাঁদের ভাষা, স্বর ও দৃষ্টিভঙ্গি ছিল স্বতন্ত্র। নিজেদের ভারী অসিত্মত্ব, শরীরী উপস্থিতি জোরালোভাবে জায়গা পেল তাঁদের ছবিতে।
কিন্তু নারী শিল্পীদের কাছে আত্মপ্রতিকৃতি হয়ে উঠল একটি সশস্ত্র ভাষার মতো। নিজস্ব গোপন একটি সন্ত্রাসের মতো। এই আন্দোলনের মধ্যে নারীরা এমন এক পৃথিবীর ঝলক দেখলেন, যেখানে আরোপিত বিধিনিষেধ না মেনে সৃজনশীল থাকা যায়, দমচাপা প্রতিবাদের ইচ্ছেগুলোর উৎস থেকে পাথরের বাঁধ সরিয়ে দেওয়া যায়। নগ্ন ও উদ্দাম করা যায় কল্পনাকে। নোঙর নামানো জাহাজের মতো অনড় ও ঠাসবুনট একটি উপস্থিতি হয়ে ছবিতে নিজের মুখ তাঁদের কাছে হয়ে উঠল অন্যতম প্রধান আইকন। যে ছবি আত্মপ্রতিকৃতি নয়, সেখানেও বারবার আসতে থাকল শিল্পীর শরীরী প্রতিমা। ফ্রিদা কাহ্লোর (১৯০৭-৫৪) ক্যানভাস তাঁর যন্ত্রণাবিদ্ধ শান্ত মুখশ্রী ধরে রাখল। মুখের বিশেষ কিছু চিহ্ন যা তাঁকে চেনায় – যেমন পাখির ডানার মতো ভুরু, আমন্ড আকারের চোখ ছবিতেও আনলেন তিনি। রিমেদিওস ভারোর (১৯০৮-৬৩) ছবিতে পানপাতার মতো মুখ, তীক্ষন নাক, দীর্ঘ মাথাভর্তি চুলের নারীর মধ্যে নির্ভুল চেনা গেল শিল্পীকে। আবার লিওনর ফিনির (১৯১৮-৯৬) আঁকা নারীরা তাদের বেড়ালের মতো কালো চোখ আর ইন্দ্রিয়াসক্ত মুখ নিয়ে হয়ে উঠল ফিনিরই চেনা মুখচ্ছবি। ১৯৩৯ সালের ‘The Alcove : An interior with three women’ ছবিতে ভারী পর্দা টাঙানো ঘরে দুজন অর্ধশায়িত মহিলা পরস্পরকে ছুঁয়ে আছেন। আর একজন মহিলা দাঁড়িয়ে। তিনজনেই যেন কোনো কিছুর প্রতীক্ষা করছেন চাপা উদ্বিগ্ন মুখে। যে তিনজন নারীর ছবি, তাঁরা যে লিওনর ফিনি, লিওনারা ক্যারিংটন এবং ইলিন অগার – এটা ছবিটিকে একঝলক দেখেই চেনা যায়। এমনকি যখন অন্য কোনো নারীর প্রতিকৃতি আঁকছেন তাঁরা, সেখানেও তাঁদের বিদ্রোহের অস্বীকারের জোরালো পাঞ্জার ছাপ এই শিল্পীরা সেইসব নারীর মুখে ঘন লাল নিম্নরেখা দিয়ে বুঝিয়ে দিতেন
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হতে ১৯৩৯ সালে অধিকাংশ পরাবাস্তববাদী বিদেশে পালিয়ে যান এবং তাঁদের মধ্যে আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও বক্তব্য নিয়ে খেয়োখেয়ি বেধে যায় । অলোচকরা মনে করেন যে গোষ্ঠী হিসাবে পরাবাস্তববাদ ১৯৪৭ সালে ভেঙে যায়, প্যারিসে “লে সুররিয়ালিজমে” প্রদর্শনীর পর । যুদ্ধের শেষে, প্যারিসে ব্রেতঁ ও মার্সেল দ্যুশঁ’র ফিরে আসার পর প্রদর্শনীর কর্তারা সম্বর্ধনা দিতে চাইছিলেন কিন্তু পুরোনো পরাবাস্তববাদীরা জানতে পারলেন যে একদল যুবক পরাবাস্তববাদীর আবির্ভাব হয়েছে, যাঁরা বেশ ভিন্ন পথ ধরে এগোতে চাইছেন । যুবকদের মধ্যে উল্লেখ্য ছিলেন ফ্রাঁসিস বেকঁ, আলান দাভি, এদুয়ার্দো পোলোৎসি, রিচার্ড হ্যামিলটন প্রমুখ ।
সুররিয়ালিজমের উদ্ভব সত্ত্বেও ডাডার প্রভাব কিন্তু ফুরিয়ে যায়নি, তা প্রতিটি দশকে কবর থেকে লাফিয়ে ওঠে, যেমন আর্পের বিমূর্ততা, শুইটারের নির্মাণ, পিকাবিয়ার টারগেট ও স্ট্রাইপ এবং দ্যুশঁ’র রেডিমেড বস্তু বিশ শতকের শিল্পীদের কাজে ও আন্দোলনে ছড়িয়ে পড়ছিল । স্টুয়ার্ট ডেভিসের বিমূর্ততা থেকে অ্যান্ডি ওয়ারহলের পপ আর্ট, জাসপার জনসের টারগেট ও ফ্ল্যাগ থেকে রবার্ট রাউশেনবার্গের কোলাঝে -- সমসাময়িক সাহিত্য ও শিল্পের যেদিকেই তাকানো হোক পাওয়া যাবে ডাডার প্রভাব, সুররিয়ালিজমের উপস্হিতি । ১৯৬৬ সালে মৃত্যুর আগে, ব্রেতঁ লিখেছিলেন, “ডাডা আন্দোলনের পর আমরা মৌলিক কিছু করিনি । ডাডা ও সুররিয়ালিজম আন্দোলনকারীদের ওপর প্রচুর চাপ সৃষ্টি করেছিল এবং কয়েকজন আত্মহত্যা করেন, যেমন জাক রিগো, রেনে ক্রেভেল, আরশাইল গোর্কি, অসকার দোমিংগেজ প্রমুখ । অত্যধিক মাদক সেবনে মৃত্যু হয় গিলবার্ত লেকঁতে ও অঁতনা আতোর ।
 সমীর রায়চৌধুরী | 122.179.172.247 | ২৪ আগস্ট ২০২১ ১৯:২২734897
সমীর রায়চৌধুরী | 122.179.172.247 | ২৪ আগস্ট ২০২১ ১৯:২২734897সমীর রায়চৌধুরী : মলয়ের অবন্তিকারা
ইলোপকন্যা
তোর বেডরুমে তোকে পেলুম না, কি ঝঞ্ঝাট, মানে হয়
অবন্তিকা, কোন নদী নিয়ে গেছে, বরফের ডিঙি ভাসালুম
দ্যাখ, কেলেঘাই চূর্ণী গুমনি জলঢাকা ময়ূরাক্ষী কংসাবতীর
স্রোতে, তোর ঘাম নেইকো কোথাও, ভাল্লাগে না, জেলেরাও
পায়নি তোর ফেলে দেয়া অন্ধছোঁয়া, পূর্ণিমাও অন্ধকারে,
কি করে চলবে বল, পেঁয়াজের কান্না নেই, ধ্যাৎতেরি
চুড়ির বাজনাহীন, চুমুগুলো কোন সপ্নে রেখে গিয়েছিস
খুঁজে পাচ্ছিনাকো, কাউকে তো বলে যাবি, মুখের প্রতিবিম্ব
আয়নাসুদ্দু ফেলে দিয়েছিলি, ওঃ কি মুশকিল, পাশে-শোয়া শ্বাস
অন্তত রেখে যেতে পারতিস, আলমারি ফাঁকা কেন, বালিশে
খোঁপার তেল নাভির তিল কাকেই বা দিলি, চেনাই গেল না
তোর মনের কথাও, টুথব্রাশে কন্ঠস্বর নেই, চটিতে নাচও
দেখতে পেলুম না, এমন কষ্ট দিস কেন অবন্তিকা, চুলের
নুটিতে থাকত ডাকনাম, ফুলঝাড়ু চালিয়েও সাড়া পাচ্ছি না,
অফিস যাবার রাস্তা এসে তোর জন্যে মাকড়সার জালে
হাতের রেখা সাজিয়ে চলে গেল তোরই মুখের ইলিশস্বাদ
নিয়ে। আরে, ওই তো, যে-ছোকরার সঙ্গে পালিয়েছিলি তুই
তারই জুতোর ছাপের স্বরলিপি মার্বেল মেঝেয় আঁকা…
মলয়ের বিখ্যাত কবিতা ‘প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার’ যে কবিতাটির জন্য মামলা-মোকদ্দমা হয়েছিল, পরবর্তীকালে আনন্দ বাগচীর ‘প্রথম সাড়া জাগানো কবিতা’ গ্রন্হে সংকলিত হয়েছে । আনন্দ বাগচী আমার কলেজ জীবনের বন্ধু । তিনি ‘কৃত্তিবাস’ পত্রিকার প্রথম দিকে যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন, পরে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মতের সঙ্গে মিল না হওয়ায় তিনি ‘কৃত্তিবাস’ পত্রিকা থেকে সরে যান । ‘প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার’ তাঁর গ্রন্হে সংকলিত করার জন্য প্রথমে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং অনুমতির প্রসঙ্গে তুলেছিলেন । মলয়ের কবিতার কোনো কপিরাইট নেই, অতএব অনুমতির প্রসঙ্গে ওঠে না । অধ্যাপক বাগচীর গ্রন্হটিও পাঠক মহলে অনায়ারে আলোড়ন তুলেছিল । কিন্তু ‘প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার’ কেন আলোড়ন তুলেছিল, কী তার বৈশিষ্ট্য, অনেকে হাংরি আন্দোলনের সময় থেকেই আমাকে প্রশ্ন করেছেন । ঢাকার একটি ওয়েবসাইটে এই কবিতাটি নিয়ে ছয় বৎসর যাবৎ তর্ক বিতর্ক চলছে ।
আমার মনে হয়েছে এই কবিতাটি বাংলা কবিতার বাঁক বদলের অন্যতম দিশাচিহ্ণ । রবীন্দ্রনাথ বাংলা কবিতার পাঠগতি বা স্পিডকে মন্থর করে দিয়েছিলেন । মলয়ের কবিতার পাঠগতি বা দ্রুতি ঢের বেশি । প্রাক-আধুনিক কবিতার গতি কবিয়ালদের বা প্রান্তিক মানুষের পদ্য, নাচ, গান ইত্যাদির মতো দ্রুতিসম্পন্ন। মলয়ের এই কবিতার শব্দ-নির্বাচন এমনই যে, সে গতি বা স্পিডকে কার্যকরী করে তুলেছে । বনলতা সেন, সুপর্ণা, নীরা এরা কবির যেন বা নিজস্ব নারী । জীবনানন্স স্পষ্টতই বলেছেন, তাঁর নায়িকা সবার নয় । ‘কী কথা তাহার সাথে, তার সাথে’, ‘ওইখানে যেওনাকো তুমি’ । কবি ও পাঠক এবং বনলতা যেন একতন্ত্রী এবং সম্পর্কের সুরে একরেখিক । ‘ছুতার’ ( ছুতোর ) দ্যোতকটি শিল্পবিরোধিতার জন্য ব্যবহার করেছেন মলয় । আর গতি স্বভাবতই চিৎকার-নির্ভর । চিৎকার এখানে ছন্দের অনুষঙ্গ । শ্বাসপ্রশ্বাসকে পাঠগতির সঙ্গে পাঠক এমনভাবে স্বয়ং ধাতস্হ হয়ে যায় যে, প্রচলিত অর্থে আমরা বলতে পারি, পাঠ-ছন্দসম্পন্ন । বরং বলা যায় কবিতাটি পপচলিত ছন্দ, থিম, প্রতীক, উপমা এসবকে গুরুত্ব না দিয়ে সেই সময়ের মেইনস্ট্রিম কবিতার প্রতি চ্যালেঞ্জরূপে আবির্ভূত হয়েছিল ।
মনে রাখা প্রয়োজন এই কবিতাটির জন্যি কবিকে রাস্তায় কোমরে দড়ি দিয়ে, হাতে হাতকড়া পরিয়ে হাঁটিয়ে-হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল থানা পর্যন্ত এবং পরের দিন থানা থেকে আদালত অব্দি । কবিতাটির ধরনধারণ ইতিপূর্বের প্রেমের কবিতার নির্ধারিত ক্যাননের সঙ্গে মেলে না ।
এই কবিতাটি সম্পর্কে লালবাজারে অভিযোগ জানিয়েছিলেন কিছু বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক । মলয় তাঁর ‘আমার জেনারেশনের কাব্যদর্শন’ এবং কবিতার বিনির্মাণ সম্পর্কে বেশ কিছু প্রবন্ধে স্পষ্টত ঘোষণা করেছিলেন, তিন থেকে পাঁচ দশক অব্দি তৈরি কবিতার পাতিবুর্জোয়া চেতনার মডেল তিনি ক্রমশ বদলে ফেলতে চান ।
প্রেম ওই কবিতার স্ট্র্যাটেজি, কেন্দ্র নয় । এজন্যই পপচলিত পাঠবোধ থেকে কবিতাটি পড়ে তাঁরা বিস্মিত হয়েছিলেন । সেই সময়ে আলোচক দীপ্তি ত্রিপাঠী আমার কবিতা পড়েও বলেছিলেন, ‘কবিতাটির মধ্যে অসংলগ্নতা রয়েছে, যুক্তিক্রম মেনে লেখা হয়নি ।’ পাটনায় থাকার সুবাদে মলয় ভোজপুরি মাগধি ইধসকে অনায়াসে কাজে লাগিয়েছিলেন এই কবিতার প্রান্তিক অবস্হান নির্ণয়ে । প্রথম পঙক্তি থেকেই কবিতাটি আক্রমণাত্মক । আধিপত্যকেন্দ্র ও প্রণালীকে বিস্হাপনের প্রয়াস । পাঠবোধকে ডিস্টেবিলাইজ করার ঝাঁকুনি । কবিতাটিকে ইচ্ছাকৃতভাবে নারী-শরীর সংশ্লিষ্ট এমন অনেক শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে যা ছয়ের দশকের আগের পাঠবোধকে বিচলিত করে ; যে পাঠবোধের মধ্যে ছিল ভালো-খারাপ, শ্লীল-অশ্লীল ইত্যাদি বাইনারিবোধ । হাংরি আন্দোলন এই বৈপরীত্যবোধকে আক্রমণ করে । ‘আমি’ হচ্ছে কবিতার মধ্যে একটি সবজান্তা দ্যোতক । এই দ্যোতকটিকেই আক্রমণ করেছেন মলয় ।
বনলতা সেন, নীরা ইত্যাদির সঙ্গে শুভাকে গুলিয়ে ফেলা উচিত হবে না । কেননা শুভা সম্পর্কে সাধারণ পাঠক যা জানতে চাইবেন তা হল কতকটা পূর্বপাঠের কবিতার নারীদের মতো । অথচ শুভা বাংলা কবিতার ঠক বিপরীত মেরুতে । যেমন খ্রিস্টধর্মে মেরি ম্যাগডালেন, তেমনই ‘প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার’ কবিতার শুভা ।
শুভা প্রধান চরিত্র নয় -- শুভার জায়গায় যেকোনো নারীবাচক নাম প্রয়োগ করা যেতে পারে । সাধারণ পাঠক শুভাকে কবিতার কেন্দ্র হিসাবে অনুমান করেন, বনলতা বা নীরার আইডেনটিটির মতো ভাবেন । মলয় তো শুভাকে কবিতার কেন্দ্র করে তোলেননি । বনলতা বা নীরা সেই কবিতার প্রাসঙ্গিক কবিতার কেন্দ্র । শুভাকে মলয়ের আর কোনো কবিতায় পাবে না । এখন তো মলয়ের কবিতায় পাঠক ‘অবন্তিকা’কে পাবেন ।
অবন্তিকাকে নিয়ে মলয় যে কবিতাগুলো লিখেছেন এবং সেই কবিতাগুলো সংকলিত করে রোহন কুদ্দুস পপকাশিত মলয়ের কাব্যগ্রন্হের নাম ‘ছোটোলোকের কবিতা’, যেখানে প্রথম কবিতার শিরোনাম ‘ডেথমেটাল’ এবং প্রথম পঙক্তি ‘মুখপুড়ি অবন্তিকা চুমু খেয়ে টিশ্যু দিয়ে ঠোঁট পুঁছে নিলি?’
মুখপুড়ি অবন্তিকা চুমু খেয়ে টিশ্যু দিয়ে ঠোঁট পুঁছে নিলি ?
শ্বাসে ভ্যাপসা চোখের তলায় যুদ্ধচিহ্ণ এঁকে ডেথ মেটাল মাথা দোলাচ্ছিস
চামড়া-জ্যাকেট উপচে লালনীল থঙ গলায় পেতল-বোতাম চোকার
ঝাপটাচ্ছিস সেক্যুইন গ্ল্যাম রকার খোলা চুল কোমরে বুলেট বেল্ট
বেশ বুঝতে পারছি তোকে গান ভর করেছে যেন লুঠের খেলা
স্ক্রিমিং আর চেঁচানি-গান তোর কার জন্যে কিলিউ কিলিউ কিল
ইউ, লাভিউ লাভিউ লাভ ইউ কাঁসার ব্যাজ-পিন কব্জি-বেল্ট
কুঁচকিতে হাত চাপড়ে আগুনের মধুর কথা বলছিস বারবার
আমি তো বোলতি বন্ধ থ, তুই কি কালচে ত্বকের সেই বাঙালি মেয়েটা ?
কোথায় লুকোলি হ্যাঁরে কৈশোরের ভিজে-চুল রবীন্দ্রনাথের স্বরলিপি
কবে থেকে নব্বুই নাকি শুন্য দশকে ঘটল তোর এই পালটিরূপ !
পাইরেট বুট-পা দুদিকে রেখে ঝাবড়া চুলে হেড ব্যাং হেড ব্যাং হেড ব্যাং
ঝাঁকাচ্ছিস রঙিন পাথরমালা বুকের খাঁজেতে কাঁকড়া এঁকে–
পাগলের অদৃশ্য মুকুট পরে দানব-ব্লেড বেজ গিটারে গাইছিস
বোলাও যেখানে চাই হাত দাও প্রেম-জন্তুকে মারো অ্যানথ্র্যাক্স বিষে
মেরে ফ্যালো মেরে ফ্যালো মেরে ফ্যালো কিল হিম কিল হিম কিল
কিন্তু কাকে বলছিস তুই বাহুতে করোটি উল্কি : আমাকে ?
নাকি আমাদের সবাইকে যারা তোকে লাই দিয়ে ঝড়েতে তুলেছে ?
যে-আলো দুঃস্বপ্নের আনন্দ ভেঙে জলের ফোঁটাকে চেরে
জাপটে ধরছিস তার ধাতব বুকের তাপ মাইক নিংড়ে তুলে
ড্রামবিটে লুকোনো আগুনে শীতে পুড়ছিস পোড়াচ্ছিস
দেয়াল-পাঁজিতে লিখে গিয়েছিলি ‘ফেরারি জারজ লোক’
ভাঙা-চোরা ফাটা বাক্যে লালা-শ্বাস ভাষার ভেতরে দীপ্ত
নিজেরই লেখা গানে মার্টিনা অ্যাসটর নাকি ‘চরমশত্রু দলে’
অ্যানজেলা গস কিংবা ‘নাইট ইউশ’-এর টারজা ট্যুরম্যান
লিটা ফোর্ড, মরগ্যান ল্যানডার, অ্যামি লি’র বাঙালি বিচ্ছু তুই
লাল-নীল-বেগুনি লেজার আলো ঘুরে ঘুরে বলেই চলেছে
তোরই প্রেমিককে কিল হিম লাভ হিম কিল হিম লাভ হিম লাভ
হিম আর ঝাঁকাচ্ছিস ঝাবড়া বাদামি চুল দোলাচ্ছিস উন্মাদ দু’হাত
পাঠক লক্ষ করবেন ‘মুখপুড়ি’ শব্দের প্রয়োগ । সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় নীরাকে এভাবে সম্বোধন করতে পারতেন না । পাঠক লক্ষ করবেন ‘মুছে’ শব্দের জায়গায় ‘পুঁছে’ শব্দের প্রয়োগ । আমার ‘টিনিদির হাত’ গল্পে আমর প্রফেসার্স লেনের বন্ধুরা ইমলিতলাকে বলতেন ‘ছোটোলোকদের পাড়া’ । এখন তো শুনছি ‘ছোটোলোকের কবিতা’ নিঃশেষিত । সাধারণ পাঠক তো অবন্তিকার পৃথক আইডেনটিটি নিয়ে ভাবতে চাইবেন না । আমার মনে হয় শুভাকে এই পরিসরের মধ্যে স্হাপন করলে আইডেনটিটি কোড পালটে যাবে । ‘প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার’ কবিতার সপ্তম পঙক্তি স্হিতাবস্হা থেকে সরে যাওয়ার ইঙ্গিতবহ --- ‘সমস্ত নোঙর তুলে নেবার পর শেষ নোঙর আমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে’। শুভার বহুরৈখিক সত্বাকে স্পষ্ট করার জন্য নন্দিতা এবং আলেয়া নাম্নী আরও দুটি নারীর উপস্হিতি রেখেছেন মলয় ।
জীবনানন্দ তাঁর কবিতায় সূর্য ও তপতীর সম্পর্কের গণিত প্রয়োগ করেছেন । সেখানে ‘সূর্যকরোজ্জ্বল’, ‘জয়জয়ন্তীর সূর্য’ ইত্যাদি শব্দবন্ধ প্রয়োগ করেছেন । ‘প্রচণ্ড বৈদভুতিক ছুতার’ কবিতায় দেখা যাচ্ছে অনভ ধরণের পঙক্তি, ‘শুভার স্তনের ত্বকের মতো বিছানায় শেষবার ঘুমোতে দাও আমায়/জন্মমূর্তের তীব্রচ্ছটা সূর্যজখম মনে পড়ছে’। বাংলা কবিতার আগে সেই সময়ের মেইনস্ট্রিমে যে নায়িকাদের অবস্হান ছিল তা মলয় বদলে দিলেন । মরিয়া মারমুখি আঞ্চলিক এথনিসিটির ভিন্নতাকে তুলে ধরলেন ।
অনুষঙ্গগুলি এযাবৎ অচেনা ছিল এই মেজাজের কবিতায় । ‘যোনিকেশরে কাচের টুকরো’, ধাবমান ছবি, আধোবোজা নারী -- কবিতাটি সময়চেতনাকে আমল দিয়েছে । এখান থেকে মলয় পরে সরে গেছেন পরিসর চেতনার দিকে । ফলে কবিতাটি সেই সময়ে, এমনকি আজও, বঙ্গীয় পাঠকসমাজের কাছে সাংস্কৃতিক সমস্যাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে । সমস্যা আজও সেই একই জায়গায় । কোথাও না কোথাও আধিপত্যকেন্দ্র স্বয়ং উপলব্ধি করেছে এই ব্লান্ট যথাস্হিতি ।
‘প্রচণ্ড বৈদভুতিক ছুতার’ কবিতাটি প্রসঙ্গে আর একটি দৃষ্টিকোণ মনে রাখতে হবে । মলয় ইংরেজি অনুবাদে নাম রেখেছিলেন ‘Stark Electric Jesus’, কারণ যিশু ছিলেন ছুতোর । কনভেন্টে পড়ার সময়ে চার্চে গিয়ে বাইবেল ক্লাস করতে হত । মলয় কবিতাটিতে খ্রিস্টধর্মের ক্যানন প্রয়োগ করেছেন । যিশুকে কাঁধে করে ক্রস বইতে হয়েছিল । মলয়কে হাতে হাতকড়া, কোমরে দড়ি বেঁধে হাঁটানো হয়েছিল । যিশুর জীবনে যেমন মেরি ম্যাগডালেন, তেমন মলয়ের কবিতায় শুভা বা অবন্তিকা । মেরি ম্যাকডালেন যিশুর প্রেমিকা ছিলেন না, জীবনের কেন্দ্রে ছিলেন না । মেরি ম্যাকডালেন ছিলেন সবার কাছে অবারিত । তিনি বনলতা সেন বা নীরার মতি সাধ্বী ইমেজে বিলং করেন না । সেদিক থেকে দেখতে গেলে কবিতার নারীকে মলয় মুক্তি দিয়েছেন, স্বাধীনতা দিয়েছেন, স্বনির্ভরতা দিয়েছেন ।
 সত্যজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় | 122.179.172.247 | ২৪ আগস্ট ২০২১ ১৯:২৩734898
সত্যজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় | 122.179.172.247 | ২৪ আগস্ট ২০২১ ১৯:২৩734898সত্যজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়: মলয় রায়চৌধুরীর উপন্যাস ও রাজনীতি
মলয় রায়চৌধুরীর তিনটি উপন্যাসের বিষয়, ভাষা ও নির্মাণকে বুঝতে চাইলে সবার আগে পাঠককে সরে আসতে হবে উপন্যাস-পাঠের প্রচলিত অভ্যাস থেকে। উপন্যাস তিনটিতেই মলয় খুব সচেতনভাবে প্রত্যাখ্যান করতে চেয়েছেন আমাদের চৈতন্যের ঔপনিবেশিকরণের ভিত্তিতে গড়ে-ওঠা উপন্যাস-ভাবনাকে। মলয়ের বয়ন-বুনন পদ্ধতি ও ভাষাতাত্ত্বিক সন্দর্ভ, বাংলা ও বিহারের প্রকৃতি, সমাজ ও ব্যক্তিমানুষের পারস্পরিক সম্পর্কসমূহের দ্বান্দ্বিক সমগ্রতাকে এবং তাদের পরিবর্তনের ধারাবাহিকতাকে অবিচ্ছিন্ন করে তুলতে চেয়েছে--- চারপাশের বাস্তবের সমালোচনা করতে-করতে ও তাকে অতিক্রম করে শিল্পের নিজস্ব বাস্তব নির্মাণ করতে-করতে।তার ফলে মলয়কে সবার আগে ভাঙতে হয়েছে প্রথাগত ইউরোপীয় কোড বা সংকেতগুলিকে। এমনকি, সেই সঙ্গে, তাঁকে সমালোচনা করতে হয়েছে, অতিক্রম করে যেতে হয়েছে, ইউরোপ থেকে আসা প্রধান আধুনিকোত্তরবাদী সন্দর্ভগুলির প্রশ্নহীন বশ্যতা ও উপযোগিতার মানসিকতাকেও।
অনিবার্য পরিণতি হিসাবে মলয়ের উপন্যাস তিনটিতে এমন এক নতুন, এতদিন আমাদের সামনে অনাবিষ্কৃত, ভারতীয় বাস্তবতার সন্ধান পাই, যাকে ঔপনিবেশিক চৈতন্য-কাঠামোর পরিসীমার মধ্যে ধারণ করা সম্ভব ছিল না। ঔপনিবেশিক শাসক ও শোষিত মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের কয়েক শতাব্দীর ধারাবাহিকতা আবিশ্বে যে-নিষ্ঠুরতা ও সাংস্কৃতিক আক্রমণ-অবক্ষয়ের জন্ম দিয়েছে--- তাকে প্রত্যাখ্যান করতে চেয়েছেন বলেই মলয়কে এই রাস্তায় হাঁটতে হয়েছে। অন্যদিকে আবার, মলয়ের বয়ন-বুনন পদ্ধতি ও ভাষাতাত্ত্বিক সন্দর্ভ কিন্তু যান্ত্রিকভাবে ইউরোপকে প্রত্যাখ্যান করে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বয়ান বা টেক্সটের মধ্যে পাঠককে সীমাবদ্ধ রাখার বার্তা প্রেরণ করে না। পক্ষান্তরে তাঁর বয়ন-বুনন পদ্ধতি ও ভাষাতাত্ত্বিক সন্দর্ভ ইউরোপীয় জ্ঞানতত্ত্ব এবং ভারতীয় স্বাধীন অভিজ্ঞান অনুসন্ধান ও সৃষ্টির আবেগ ও স্পন্দনশীলতার দ্বান্দ্বিক সংশ্লেষের পরিণতি। মলয় তাঁর নিজের মতো করে, তাঁর উপন্যাস তিনটিতে ধারাবাহিকভাবে, ঔপনিবেশিকতার দায়মোচনের প্রক্রিয়াকে বিকশিত করে তুলেছেন। তা করতে-করতে তাঁর উপন্যাসের বয়ান একই সঙ্গে ধারণ করেছে আধিপত্যকামী কেন্দ্রীয় ব্যবস্হাসমূহ ও তাদের বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়ে-থাকা প্রান্তীয় শক্তিসমূহের দ্বান্দ্বিকতাকে এবং ওই কেন্দ্রীয় ব্যবস্হাসমূহ থেকে উৎপন্ন মহাসন্দর্ভ ও প্রান্তীয় বর্গের প্রতিদিনের যাপিত জীবনের গভীর থেকে উৎসারিত বিকল্প সন্দর্ভের দ্বান্দ্বিকতাকে।
দুই শতকেরও বেশি সময় ধরে, আমাদের যে প্রত্যক্ষ ইউরোপীয় নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকতে হয়েছিল--- সেই সত্যকে আমরা বাদ দিতে পারি না। ভুলে থাকতে পারি না, পাশ কাটিয়ে যেতে পারি না। তার পাশাপাশি আবার প্রাক-ঔপনিবেশিক পর্বে ফিরে যাবার চেষ্টা করেও ঔপনিবেশিকতাকে প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব নয়। মলয় তাই তাঁর এই উপন্যাস তিনটিতেই ইউরোপীয় সন্দর্ভগুলিকে এবং সেই সঙ্গে ইউরোপ ও ভারতবর্ষের ক্রিয়া-প্রতিক্রয়ার মধ্যে অবস্হানকারী সুবিধাভোগী অংশের দ্বারা উৎপাটিত সন্দর্ভগত সক্রিয়তাকেও ইন্টারোগেট করেন। সেই সূত্রে তিনি বুঝে নিতে চান, ইউরোপ কেমনভাবে মতাদর্শগত আধিপত্য পপতিষ্ঠার সূত্রে তাদের কোড বা সংকেতগুলিকে আমাদের সামাজিক ব্যবস্হার প্রবহমানতার মধ্যে গ্রহণযোগ্য করে তুতে পেরেছিল, এবং এখনও কেন পারছে। এইভাবে বুঝে নিতে চাইবার পরিণতিতে, আধিপত্যকামী সন্দর্ভের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে, মলয়কে নির্মাণ করে নিতে হয়েছে বিকল্প সন্দর্ভের এমন এক পরিসর যা ঔপনিবেশিকতার প্রভাবমুক্ত জাতীয় ও আঞ্চলিক উপাদানের দ্বারা সম্পৃক্ত এক সচল চিন্তাপ্রবাহের দ্বারা নির্ধারিত। এই চিন্তাপ্রবাহের সূত্রেই মলয়ের বিকল্প সন্দর্ভ প্রতিনিয়ত শুষে নিচ্ছে চারপাশের নিরুচ্চার বর্গের জীবন থেকে স্বতোৎসারিত বিভিন্ন জায়মান কোড বা সংকেতগুলিকে, এবং সেই সঙ্গে শিল্পের নিজস্ব পরম্পরা এবং শৃঙ্খলার সূত্রেই তা ক্ষয়িত করে বাংলা উপন্যাসের প্রচলিত আধিপত্যকারী সন্দর্ভকে।
মলয়ের উপন্যাস তিনটির ভাষাতাত্ত্বিক সন্দর্ভ ও বয়ন-বুনন পদ্ধতি উপন্যাস সম্পর্কে কোনও বিশ্বজনীন সাহিত্যিক ধারণাকে স্বীকার করে না। তাই প্রচলিত মহাসন্দর্ভের পরিসীমার বাইরে দাঁড়িয়ে মলয়কে তাঁর চারপাশের বাস্তব পরিস্হিতির সঙ্গে নতুন ধরণের নির্ধারক সম্পর্ক নির্মাণ করে নিতে হয়েছে। তা করতে গিয়ে মলয় কিন্তু খুব সচেতনভাবে এসেনশিয়ালিজমের বিপদকে এড়িয়ে গেছেন। ঔপনিবেশিকতা ও পণ্যমোহের চাপে ধ্বস্ত মধ্যবিত্তের হাহাকার ও প্রান্তীয় মানুষের আর্তনাদকে তিনি এমন নির্মমভাবে উন্মোচন করেন এবং নারী-পুরুষের যৌন সম্পর্ককে ও যৌন আকাঙ্খার অবদমনকে ক্ষমতাকাঠামোর সঙ্গে সম্পর্কিত করে--- এতদিন পর্যন্ত প্রতিনিধিত্বহীন এমন দৃষ্টিভঙ্গী ও ভাষায় ধারণ করেন যে, তাঁর পক্ষে এসেনশিয়ালিজমের বিপদকে অতিক্রম করে যাওয়া অনিবার্য হয়ে উঠেছিল।মলয়ের ভাষাতাত্ত্বিক সন্দর্ভের নিজের ভিতরই এমন কিছু বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান, যার শক্তিতে তিনি পরিপার্শ্বের সঙ্গে নতুন ধরণের নির্ধারক সম্পর্ক নির্মাণ করে নিতে পারেন। তার ফলে, মলয় একদিকে যেমন সাহিত্য-বিষয়ক বিশ্বজনীন আধিপত্যকারী ধারণাসমূহকে প্রত্যাখ্যান করতে পারেন, আবার অন্য দিকে, অর্থ বা মিনিং উৎপাদনের ক্ষেত্রে, সংযোগের ক্ষেত্রে, আত্তীকরণের ক্ষেত্রে, উপন্যাস পাঠের প্রচলিত-সজ্ঞায়িত সীমাকে ভেঙে ফেলে নতুন দেশজ রাজনৈতিক বাস্তবতা ও তজ্জনিত নবোথ্থিত অভিঘাতকে ধারণ করতে পারেন --- উপন্যাসের সন্দর্ভে তাকে সঞ্চালিত করতে পারেন।
মলয় রায়চৌধুরী অর্থ-উৎপাদন, সংযোগ ও আত্তীকরণের ক্ষেত্রে বিকল্প সন্দর্ভের ওপর নির্ভর করেন বলেই তাঁর উপন্যাস তিনটির সঙ্গে কোনো সুপরিচিত বাণিজ্যসফল পত্রিকা বা প্রকাশনার নাম জড়িয়ে থাকে না।'ডুবজলে যেটুকু প্রশ্বাস' ছাপা হয়েছিল 'হাওয়া৪৯' পত্রিকায়, 'জলাঞ্জলি' ছাপা হয়েছিল 'রক্তকরবী' পত্রিকায়, ও 'নামগন্ধ' প্রকাশ করেন ঢাকার 'সাহানা' প্রকাশন সংস্হা। সংস্কৃতি উৎপাদন কারখানার দ্বারা উৎপাদিত পণ্যগুলির উৎপাদন পদ্ধতির প্রধান দুটি বৈশিষ্ট্য হল: প্রমিতকরণ ও নকল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ। মলয় রায়চৌধুরী এই দুই বৈশিষ্ট্যকে প্রত্যাখ্যানের সূত্রে, আসলে প্রত্যাখ্যান করেন সেই সন্দর্ভে স্বচ্ছন্দ বোধ-করা আশুতোষ পাঠক-কুলকেও। মলয়ের সন্দর্ভে প্রবেশ করতে চাইলে মেরুদণ্ডকে ঋজু রেখেই প্রবেশ করতে হবে। দেশ-কাল সম্পর্কে মলয় তাঁর গভীর জিজ্ঞাসাকে হাজির করতে চান বলেই --- তাঁর উপন্যাসের পাঠককেও কোনও-না-কোনও ভাবে এক ধরনের জিজ্ঞাসার দ্বারা আলোড়িত হবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখতে হবে। নতুন রুচির সঙ্গে দ্বিরালাপে অনীহ পাঠকের জন্য মলয়ের সন্দর্ভ নয়।
'ডুবজলে যেটুকু প্রশ্বাস'-এ পাটনার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সূত্রে মলয় আমাদের দাঁড় করিয়ে দেন গোটা বিহারের জাতি, বর্ণ ও শ্রেণীসম্পর্কের আবহমান জটিল নেটওয়র্কের সামনে। মলয় বিহারের সামাজিক কাঙামোর বিভিন্ন স্তরে অবস্হানকারী জাতি ও বর্ণের পারস্পরিক সম্পর্কসমূহের দ্বান্দ্বিক সমগ্রতার সূত্রে গড়ে-ওঠা সামাজিক গতিশীলতাকে বুঝে নিতে চেয়েছেন। বিহারের এই সামাজিক গতিশীলতার সঙ্গে আঞ্চলিক উৎপাদন-ব্যবস্হা ও বৃহৎ পুঁজির সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন। এই সামাজিক গতিশীলতা একান্তভাবেই ভারতীয় সমাজের ও ইতিহাসের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। বিহারের ধর্ম ও বর্ণের লড়াইয়ের মাঝখানে পড়ে বাঙালিদের অবস্হা খুবই করুণ। হয় তাদের বিহার থেকে চলে আসতে হচ্ছে, অথবা নিজস্ব সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞানের বিষয়ে সচেতনতাকে বর্জন করতে হচ্ছে। 'সাংস্কৃতিক চাপ থেকে চাগিয়ে-ওঠা অসহ্য দুঃখের খতিয়ান রাখে না কোনও ভূভাগের ইতিহাস। মিলিয়ে যায় হরপ্পাবাসী বা মিশরীয়র মতন।' শিলচরের বাঙালিদের এক ধরনের সংগঠিত প্রতিবাদ আছে। বিহারে কিন্তু এখন বাঙালি পরিবারের ছেলে-মেয়েদের হিন্দি বা ইংরেজি মাধ্যম ছাড়া অন্য মাধ্যমে লেখাপড়ার সুযোগ প্রায় নেই।
রিজার্ভ ব্যঙ্কের নোটগুনিয়েদের সূত্রে ক্ষমতা-কাঠামোর অভ্যন্তরীন চরিত্র ও নানা ধরনের দুর্নীতির সন্ধান পাওয়া যায়। বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির বিবরণের মধ্যে মলয় আমাদের সচেতন করেন মানুষের শ্রমশক্তি ও কাগজের নোটের মধ্যেকার সম্পর্ক বিষয়ে। 'অতনুকে ছাড়ে না পচা নোটের জীর্ণ গন্ধ, যে-গন্ধে ওর চারিদিকে ঘনিয়ে চলেছে দুর্বহ স্বচ্ছ অন্ধকার। পোড়াবার সময়, চুল্লি থেকে ভেসে আসে মড়া পোড়াবার হুবহু গন্ধ, অথচ ছাইয়ের রং সোনালি। চুল্লিতে নোট ফেলার সময়ে ননীদা হরিবোল দেন, রাণা রামদেও সিং আওয়াজ দিয়ে ওঠে রাম নাম সৎ হ্যায়'। হরিবোল আর রামনামের সূত্রে নোটের দহন--- মানুষের দহনের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন হয়ে ওঠে। কারণ অর্থ হল বিনিময়ের গতিপথে আবশ্যিক প্রয়োজন থেকে গঠিত স্ফটিকস্বরূপ, তার দ্বারাই শ্রমোৎপন্ন বিভিন্ন দ্রব্য কার্যত পরস্পরের সঙ্গে সমীকৃত হয়, এবং এই ভাবে কার্যক্ষেত্রে পণ্যে পরিবর্তিত হয়।যে-হারে মানুষের শ্রমশক্তি দ্বারা উৎপাদিত দ্রব্য পণ্যে পরিণত হয়, ঠিক সেই হারেই একটি বিশেষ পণ্য পরিণত হয় অর্থে। অর্থও যে একটা পণ্য এটা বোঝা তেমন মুশকিল নয়। কিন্তু পণ্য কেন ও কী ভাবে অর্থে পরিণত হয় তা জানা গেলেই বোঝা যায়--- নোট পোড়াবার সময়ে মানুষ পোড়ানোর গন্ধ পাওয়া যায় কেন। অর্থ পণ্যকে প্রমেয় করে না। ব্যাপারটা তার উল্টো। মূল্য হিসেবে সমস্ত পণ্যই মনুষ্য-শ্রমের বাস্তব রূপ, সুতরাং প্রমেয়, সেই কারণেই একটিমাত্র বিশিষ্ট পণ্যের সাহায্যে সেই মূল্যের পরিমাপ করা চলে, এবং উক্ত বিশিষ্ট পণ্যটিকে পরিণত করা যেতে পারে সেগুলির মূল্যের সাধারণ পরিমাপে, বা অর্থে। পণ্যের মধ্যে যে মূল্যের পরিমাপ, শ্রমসময় অন্তর্নিহিত থাকে তাকে অবশ্যই যে বাহ্যিক রূপ ধারণ করতে হবে, মূল্যের পরিমাপ হিসেবে অর্থ সেই বাহ্যিক রূপ।অর্থের ভিতর পণ্যের মূল্য স্বতন্ত্র সত্তা লাভ করে বলেই তো অর্থ সঞ্চালনের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।কাজেই, সঞ্চালনের মাধ্যম হিসেবে অর্থের গতি আসলে মানুষের শ্রমশক্তি দ্বারা উৎপন্ন পণ্যের নিজ রূপেরই গতি। সেই কারণেই একই মুদ্রা, বিক্রেতার হাতে আসে পণ্যের হস্তান্তরিত রূপ হিসাবে, এবং আবার তার হাত ছেড়ে চলে যায় পণ্যের পরম হস্তান্তযোগ্য রূপ হিসেবে। অর্থ যে মুদ্রার আকার ধারন করে সেটা হয় সঞ্চালনের মাধ্যম হিসেবে তার কাজের দরুন।পণ্যের দাম বা অর্থ-নাম দিয়ে কল্পনায় সোনার যে-ওজনের পরিচয় দেওয়া হয়, তাকে সঞ্চালনের ভেতরে, মুদ্রার আকারে অথবা এক নির্দিষ্ট মূল্যের সোনার টুকরোর আকারে অবশ্যই সেই সমস্ত পণ্যের সম্মুখীন হতে হয়। দামের মান নির্ধারণের মতো মুদ্রা নির্মাণও রাষ্ট্রের কাজ। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তাই প্রত্যক্ষ রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণেই থাকে। রাষ্ট্র কতগুলি কাগজ সঞ্চালন-ক্ষেত্রে ছাড়ে, তার ওপর এক টাকা থেকে ৫০০ টাকা পর্যন্ত বিভিন্ন অর্থ-নাম ছাপা থাকে। কাগজি অর্থ--- সোনা কিংবা অর্থের প্রতিনিধিত্বমূলক একটি প্রতীক। তার সঙ্গে পণ্যের মূল্যের সম্পর্ক এই যে, মানুষের শ্রমশক্তি দ্বারা উৎপাদিত পণ্যের মূল্য ভাবগতভাবে যে-পরিমাণ সোনায় প্রকাশিত হয়, কাগজ তারই প্রতীকী পরিচয় বাহী। এভাবেই কাগজের নোট মানুষের শ্রমশক্তি দ্বারা সৃষ্ট মূল্যের প্রতীক হয়ে ওঠে। তাই নোট পোড়ানোর সময়ে মড়া পোড়ানোর গন্ধ, হরিবোল আর রামনাম গভীরভাবে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে।
আমাদের ঔপনিবেশিক অস্তিত্ব আর চৈতন্যের ঔপনিবেশিকীকরণকে প্রবলভাবে সমালোচনা করেন মলয়, রাজগিরের একটি বাড়িতে 'ল্যাংটো পাথরের এলিয়ে পড়া' নারীমূর্তির একই সঙ্গে বর্ণনা ও সমালোচনার সূত্রে।'আম্রপালীর উরু আর নিতম্বে গড়া ভেনাস। উর্বশীর খোলা স্তন মেলে হেলে রয়েছে হেলেন অব ট্রয়। শকুন্তলার কটাক্ষ বিলোচ্ছেন মার্বেল-পাথরের শীতল ক্লিওপেট্রা। দেশ ছেড়ে যেতে পারেনি এসব জারজ মেমের দল'। (ডুবজলে পৃ ৭৫) আবার সমাজের উচ্চবর্ণের মানুষদের আমেরিকা যাত্রা ও রজনীশের আশ্রমে আমেরিকান নারীদের সঙ্গে যৌনসংসর্গ করাকে যুক্তি সম্মত করে তোলা হয় তৃতীয় দুনিয়ার বহু ব্যবহৃত সাম্রাজ্যবাদ 'বিরোধী' কিছু শব্দকে ব্যবহারের মাধ্যমে। 'চন্দ্রকেতু সিং দশ হাজার টাকা খরচ করে আমেরিকান মাগিদের ঠুকে আসছে রজনীশ আশ্রমে ফি-বছর একবার। বলছিল যে পেন্টাগন, সি আই এ, এম এন সিদের ঠুকছে মনে করে চাপে মাগিগুলোর ওপর।' (ডুবজলে পৃ ৮১)। আবার সরকারি পয়সায়, রেমিটান্স নিয়ে যাবার সূত্রে, আশ্রয় পাওয়া যায় 'ভূতল দেহগ্রাহকের পান্হশালা'-য়। খাদ্য, পানীয় ও নারীদেহ জোগানোর একটি অঘোষিত সরকারি ব্যবস্হা আছে--- সরকারি পয়সায়। আবার পাঁচদিন বা পনেরোদিন বা একবছরের জন্যে বদলি হয়ে বা ট্রেনিং-এর জন্য ইংল্যান্ড, আমেরিকা, মিশর, ফিলিপিন্স বা থাইল্যান্ড যাবার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আধিকারিকদের ভিতরে যে ল্যাং মারামারি চলে তার বর্ণনা প্রসঙ্গে মলয় চমৎকার মন্তব্য করেন: 'কতো রকমের যে বিদেশি ভিক্কে পাওয়া যায় তৃতীয় বিশ্বে।' ( জলাঞ্জলি ৯৭)। অভিন্ন ক্ষমতাকাঠামোর মধ্যে দাঁড়িয়ে ঊর্ধতন ও অধস্তন পদাধিকারীর মধ্যে আলোচনার সূত্রে গোটা উন্নত বিশ্বের বিভিন্ন শহরের পতিতালয়গুলির গলিঘুঁজির খবর ও যৌন অভিজ্ঞতার আদান-প্রদান অবাধে চলতে থাকে। মলয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্মীদের জ্ঞান ও ক্ষমতার সঙ্গে তাদের যৌন জীবনকেও অন্বিত করে দেন। যার পরিণতিতে বহিরঙ্গে এক আপাত-বোহেমিয়ান আচার-আচরণের মধ্যেও অন্তরঙ্গ স্তরে নিঃশব্দে প্রবাহিত হতে থাকে ঔপনিবেশিকতার ধারাবাহিকতার সত্য ও তার মলয়কৃত সমালোচনা।
মলয়ের এই সমালোচনার সূত্রে স্পষ্ট হয় ক্ষমতা মদমত্ত ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্হা যৌনজীবনের ওপর বিভিন্ন কৃৎকৌশল চাপিয়ে দিয়ে নিয়ন্ত্রণকে কেমনভাবে সর্বব্যপ্ত করে তুলতে চায়। মলয় দেখিয়ে দেন যৌন-নৈতিকতাও কেমনভাবে ক্ষমতার নির্মিতি হয়ে ওঠে। ক্ষমতার সূত্রে, মতাদর্শগত আধিপত্যের সূত্রে, মানুষের আত্মপ্রশিক্ষণের সূত্রে, শৃঙ্খলা আরোপিত হয় শুধু বহিবৃত স্তরে নয়, সেই সঙ্গে অন্তর্বৃত স্তরেও। যৌনতাকে নিয়ন্ত্রণের কৃৎকৌশল আসলে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্হার অস্তিত্বরক্ষার প্রাকরণিকতার সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন। মলয় তাঁর তিনটি উপন্যাসেই বারবার দেখান--- যৌন আবেগের তীব্রতাকে নিয়ন্ত্রণ করে কেমনভাবে প্রচলিত সামাজিক স্হিতাবস্হাকে বাঁচিয়ে রাখা হয়, প্রান্ত ও কেন্দ্রকে মিলতে দেওয়া হয় না। যখনই এই নিয়ন্ত্রণ ভাঙতে চাওয়া হয় বা প্রান্ত ও পরিধি মিলতে চায়--- তখনই ভেঙে পড়ে সামাজিক ও মনস্তাত্বিক জগতের আপাতগ্রাহ্য শৃঙ্খলাগুলি, এসে যায় উন্মাদনা আর দুর্ঘটনা। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্হার বিভিন্ন কৃৎকৌশলের সূত্রে যৌনসম্পর্কের ওপর দাম্পত্যের একচ্ছত্র অধিকার সামাজিক স্বীকৃতি পেয়ে যায়।তার ফলে দাম্পত্য সম্পর্কের বাইরে অন্য কোনও সম্পর্কের সূত্রে উৎপাদিত সন্তানের সামাজিক স্বীকৃতির সমস্যা এই ইনটারনেটের যুগেও বিদ্যমান।তার ফলে আমাদের যৌন-নৈতিকতার ধরনা যৌনতা ও দাম্পত্যে অনোন্যসম্পৃক্ত হয়ে আবর্তিত হচ্ছে।
মলয়ের তনটি উপন্যাসের অনেক চরিত্রই এই আবর্তনের শৃঙ্খলার বাইরে চলে যেতে চায়। অথচ ধনতান্ত্রিক ব্যবস্হা যৌন-প্রক্রিয়াকে সন্তান উৎপাদনের প্রক্রিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে তাকে করে তুলতে চাইছে একবাচনিক। এই টানাপোড়েনের মধ্যেই মলয়ের উপন্যাসগুলি যে-নির্মম সত্যকে উন্মোচন করে তা হল--- আমাদের যৌন জীবনের পরিসর হচ্ছে মানবিক গতি ও স্হবিরতার দ্বিবাচনিক সম্পর্কের পরিসর, ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামোর মতাদর্শগত আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পরিসর। ব্যক্তিসত্তা প্রচলিত ব্যবস্হার সামনে আত্মসমর্পণ করে 'সামাজিক' ও 'নেতিক' হয়ে উঠেছে--- আবার কখনও প্রচলিত ব্যবস্হাকে ভেঙে সমাজের সঙ্গে ব্যক্তিসত্তার বহুস্বরিক দ্বিবাচনিক সম্পর্ক গড়ে উঠছে।
ননীগোপালের বিয়ের রাত্রে সব কথার উত্তরে অরিন্দম বলেছিল 'না'। শিমুলতলা থেকে ফিরবার পরে পুরো উন্মাদ হয়ে গেল। তার দু-বছর আগে থেকে পাশের ফ্ল্যাটের সাত বছরের বড় এক পীনোন্নত মহিলার সঙ্গে দুমদাম অফিস পালিয়ে দুপুর কাটাচ্ছিল অরিন্দম। 'মহিলা আসল কাজটা করতে দিচ্ছেন না অথচ চলছে দু-বছর'। অরিন্দমের স্বীকারোক্তি এই রকম: 'মিধ্যে নিয়েই কী গভীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে, অসহ্য।...অথচ জীবনের বিরুদ্ধে আমি কিছুই করিনি। পালাতে হবে। দুঃখের নিজস্ব আনন্দ থেকে পালাবো।...জানাজানি হয়ে গেলে আত্মহত্যা ছাড়া উপায় নেই।...কলকাতায় বদলির দরখাস্তটা মঞ্জুর হয়ে গেলে বেঁচে যেতুম।' আবার মানসিকভাবে, প্রথাগত অর্থে, 'সুস্হ' হয়ে কাজে যোগ দেবার পর সে আবার স্বীকার করে: 'ছাড়াতেই পারছিলুম না নিজেকে। ভালো লাগাটাই খারাপ লাগতে আরম্ভ করেছিল।' তারই পাশাপাশি সহকর্মীদের বলে: 'যখন পাগল ছিলুম তখন দশ টাকার রুপোর কয়েন বেরিয়েছিল। আমার জন্য রেখেছে কি না ।' ( ডুবজলে পৃ ৩৭ )। অরিন্দমের আখ্যান এভাবেই ধারণ করে সমাজের সঙ্গে ব্যক্তিসত্তার দ্বিবাচনিকতাকে; প্রচলিত যৌন সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে আসার আকাঙ্খা, আবার তার পরেই, প্রচলিত ব্যবস্হার সামনে নতজানু হবার মধ্যবিত্ত অনিবার্যতাকে। আবার এই নতজানুত্বই মানুষকে মানসিকভাবে 'সুস্হ' বলে প্রমাণ করে।
মলয়ের এই উপন্যাস তিনটিতে আকাঙ্খার রাজনীতির দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিসর দৃশ্যমান হয়--- চরিত্রগুলি বিপরীতধর্মী দৃষ্টিভঙ্গীর কারণে। এক দিকে মানসী বর্মণ চাকরি ছেড়ে দিয়ে তার ডাক্তার স্বামীর কাছে চল;এ যায় নওয়াদায় ওয়ারিশ আলি গঞ্জে। এলাকাটা 'বিনোদ মিশ্র-র নকশালদের গড়'। মানসীর স্বামী সেখানে ডাক্তারির সঙ্গে সঙ্গে নিচু জাতের লোকের মধ্যে বিপ্লবের প্রচার করেন। তার ডাক্তারখানাই মাওবাদী কমিউনিস্ট সেন্টারের ক্রান্তিকারী কিষাণ সমিতির অফিস। ননীগোপালও চলে গেছে ওদের কাছে। মুসহরদের সন্তানদের অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন করতে থাকে মানসী। গয়া, জাহানাবাদ, অওরঙ্গাবাদ, নওয়াদার গ্রামে বন্দুকধারী যুবকরা থাকে তার পাহারায়। ননীগোপাল সাইকেলে এ-গ্রাম সে-গ্রাম করে মাথায় গামছা বেঁধে। রসিক পাসওয়ানের সঙ্গে গাড়ি চালিয়ে পাটনা থেকে কলকাতা আসবার সময়ে অরিন্দম আবিষ্কার করে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে তার প্রাক্তন সহকর্মী নিরুদ্দেশ হয়ে-যাওয়া অতনুকে--- নকশাল অধ্যুষিত অঞ্চলে নিম্নরর্ণের মানুষদের এক ঘণবিবাহের অনুষ্ঠানের পুরোহিত হিসেবে। 'ইংরেজিতে মন্তর পড়ছে, পরিষ্কার ভালো ইংরেজিতে আর আবোল-তাবোল উচ্চারণে সেগুলো তারস্বরে ওগরাচ্ছে হবু স্বামী-স্ত্রী।...ইংরেজিতে কী পাঠ করছে কান পেতে শোনে অরিন্দম আর স্তম্ভিত হয়ে যায়। চিনে ছাপানো 'রেড বুক' থেকে উদ্ধৃতি পাঠ করছে...।' ( জলাঞ্জলি পৃ ৪২ )।
আবার অন্যদিকে আকাঙ্খার রাজনীতির ভিন্ন পরিসর দৃশ্যমান হয় ইন্দ্রাণী সাধুখাঁ'র কেরিয়ার সচেতনতা এবং অভিজিৎ-সুজাতার সম্পর্কের সূত্রে।চাকরির সূত্রে ইন্দ্রাণী সাধুখাঁ ও অভিজিৎ লশকর ইন্সপেকশানে এসে যে-বাড়িতে আশ্রয় পায়, সে-বাড়ির মালিক ও তার ছেলে কাঠমান্ডুতে থাকে ও সেখানে ক্যাসিনো চালায়। ইন্দ্রাণী ও অভিজিৎ-এর দেখাশোনা করে কেয়ারটেকার অমরুতমল লোঢ়া। করয়ারটেকার রোজ তাদের বিহারের ওই অঞ্চলের আঞ্চলিক ইতিহাস শোনায় মৌখিক ইতিহাসের আকরণে। তারই মধ্যে আশ্রয়দাতার নিঃসন্তান পুত্রবধু সুজাতার সঙ্গে অভিজিৎ-এর মানসিক ও দৈহিক সম্পর্ক তৈরি হয়। সুজাতা গর্ভিণী হয়। পরে অভিজিৎ জানতে পারে সুজাতার শ্বশুরের সন্তান-উৎপাদন ক্ষমতা না থাকার ফলে অমরুতমলই সুজাতার স্বামীর জন্মদাতা। আবার সুজাতার স্বামীরও একই সমস্যা থাকার ফলে সুজাতার গর্ভে অভিজিৎ-এর সন্তান এল, অমরুতমল ও সুজাতার শ্বাশুড়ির পরিকল্পনার সঙ্গে সুজাতার অভিনয়ের পরিণতিতে। প্রতারিত অভিজিৎ বলে, 'অমরুতমল জানতো, শাশুড়ির সমর্থন ছিল, পুরো নাটকটা উদ্দেশ্যপূর্ণ, শুধু ব্যবহৃত হলুম আমি আর বেচারা অনাবাসী স্বামী।' ( জলাঞ্জলি পৃ ৯০ )।
ম্যানিলা যেতে উচ্চাকাঙ্খী ইন্দ্রাণী, অভিজিৎ-এর এই অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বলে, 'তুমি এভাবে নিজেকে জড়াচ্ছ কেন ঘটনাটার সঙ্গে, বলো তো ? ওদের একটা লেজিটিমেট বাচ্চা চাই। নল-খোকা, ল্যাবরেটারি-খুকু না করে এই উপায়ে হলে ক্ষতি কি ? কেলেঙ্কারি হল না কোনও।' ( জলাঞ্জলি পৃ ৯০)। ফিরবার পথে, ট্রেনে ওঠার আগে, রেলস্টেশনে, সুজাতার শাশুড়ি অভিজিৎ-এর হাতে লক্ষাধিক টাকা দামের একটি হিরের আঙটি পরিয়ে দেন। ট্রেনে উঠে ইন্দ্রাণী ওপরের বার্থে রহস্য উপন্যাসের ডুবে থাকতে-থাকে দেখে ট্রেন বারাউনি থেকে হাতিদহের দিকে যাবার সময় ট্রেনের জানলা তুলে অভিজিৎ আঙটিটা নদীতে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। কেরিয়ার সচেতন ইন্দ্রাণী 'বললে না কিচ্ছু। লাঘব করা যাবে না। অন্যের ছোঁয়াচে কষ্টের মুখোমুখি পড়ে গেলে, নিজের যাতনা বেড়ে যেতে পারে। মোহমুক্তো ওভাবে হয় না। শীতকে জাঁকিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে, গলা ওব্দি কম্বল টেনে, অভিজিৎ-এর অসুখ যাতে না ওর নিজেরই উপসর্গ হয়ে ওঠে, রহস্যোপন্যাসে ফিরে যায় ইনি ( ইন্দ্রাণী)।' (জলাঞ্জলি পৃ ৯১)।
পরবর্তী অন্য একটি ইন্সপেকশনের সময়ে, ধানবাদে প্রবল বৃষ্টির মধ্যে হোটেলের বাইরে সম্পূর্ণ উলঙ্গ অনুর্ধ পঁচিশ এক উন্মাদিনীকে দেখে অভিজিৎ ইন্দ্রাণীকে রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ ডেকে তোলে উন্মাদিনীকে জামাকাপড় পরাবার প্রস্তাব নিয়ে। 'ইনি ভেবেছিল স্বাভাবিক হয়ে এসেছে অভিজিৎ। দেখা যাচ্ছে ওর তো রাত্তিরে ঘুম আসে না। জানালায় দাঁড়িয়ে থাকে মাঝরাতে।...কিসের যে তাগিদ অনুভব করছে ও ।' (জলাঞ্জলি পৃ ১০৯)। ধানবাদ থেকে ফিরে ইন্দ্রাণী জানতে পারে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তাকে ম্যানিলা পাঠাচ্ছে। আর অভিজিৎ চলে যায় উন্মাদ আশ্রমে। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্হায় এই দুটি পরিণতিই যেন অনিবার্য ছিল।যে যত বেশি সুশৃঙ্খল হবে তার তত উথ্থান আর যে যত আবেগতাড়িত প্রবৃত্তিচালিত সে তত বেশি-বেশি করে চলে যাবে কেন্দ্র থেকে দূরে, মার্জিনে। প্রচলিত মহাসন্দর্ভের সামনে যাঁরা নতজানু হন না, কোনও না কোনও ভাবে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্হা তাদের উন্মাদ হিসেবে চিহ্ণিত করবেই।'পাগলা-পাগলিদের লোকে বাড়ি থেকে তাড়ায়। শহরের ভিতর থেকে হ্যাট-হ্যাট হাঁকিয়ে, শহরের বাইরে পাঠিয়ে নিশ্চিত হতে চায় সবাই। ল্যাংটো হলে বেড়ে যায় হ্যাট-হ্যাটের মাত্রা। ব্যবসাকেন্দ্র থেকে ভাগিয়ে ঠেলে দেয়া হয় আড়ালে-আবডালে। বড়লোক পাড়ায় ঢুকে গেলে, সেখান থেকে তাড়িয়ে গরিব পাড়ার দিকে। তারপর আর দেখা যায় না।কোথায় যে ওরা উবে যায়!'(জলাঞ্জলি পৃ ১১০)।
মলয়ের উপন্যাসে একদিকে অতনু-মানসীদের জগৎ, অন্যদিকে অভিজিৎ-অরিন্দমের জগৎ। আকাঙ্খাকে যথাপ্রাপ্ত কাঠামোর স্তরে নামিয়ে আনতে চায়নি।আকাঙ্খা নিজেই নিজের মধ্যে এক নতুন বাস্তব বানিয়ে তুলেছে। আর সেই সূত্রেই উক্ত দুই জগতের বাসিন্দারাই একই সঙ্গে অতিক্রম করে যায় যথাপ্রাপ্ত প্রতিমা ও কল্পনার সীমাকে। একইভাবে আকাঙ্খা একটি শাস্ত্রীয় নির্দেশ লঙ্ঘনকারী শক্তিতে পরিণত হয়। তার ফলে বোঝা যায়--- আকাঙ্খা বিধিনিষেধের জন্ম দেয় না, পক্ষান্তরে বিধিনিষেধই আকাঙ্খার জন্ম দেয়। অতনু-মানসীরা আকাঙ্খার রাজনীতির মোকাবিলা করতে চায় শ্রেণীগত অবস্হান থেকে। আর অন্যদিকে অরিন্দম-অভিজিৎরা তা করতে চায় বিষয়ীনির্ভর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। বিষয়ীনির্ভর দৃষ্টিভঙ্গি আকাঙ্খার অযৌক্তিক পরিমন্ডলকে গুরুত্ব দিয়ে সামাজিক উৎপাদনের যুক্তিবাদী বিশ্বকে অস্বীকার করতে চায়। অন্যদিকে শ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গি--- সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক, দুই ধরনের দমনকেই একটি অভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্যে অবিচ্ছিন্নভাবে বুঝতে চায়।শ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গি আকাঙ্খা উৎপাদনের সূত্র ধরে যে সমগ্রতার ধারনা গড়ে তুলতে চায় তা সবসময়েই এক ধরনের পরিবর্তন-প্রবাহের মধ্যে সচল থাকে।অভিজিৎ-অরিন্দমের ধনতান্ত্রিক শৃঙ্খলাকে অতিক্রমের আকাঙ্খা কোনও বিকল্প সমগ্রতার ধারণা ও সচলতার সঙ্গে সংলগ্ন হয় না বলেই--- তাদের বিষয়ীনির্ভর আকাঙ্খার রাজনীতি ধনতান্ত্রিক সমগ্রতাধর্মী চিন্তা এবং আমাদের সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক কাঠামোর অনমনীয়তার বিরুদ্ধে যত তীব্র প্রতিক্রিয়া হিসেবেই গ্রাহ্য হোক না কেন --- তা কিন্তু ওই প্রতিক্রিয়ার সূত্রেই ওই সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক কাঠামোগুলির যাথার্থ্যকেই প্রমাণ করে।দ্বান্দ্বিক অবস্হান থেকে দেখলে বোঝা যায়--- চরম ভিন্নতা, বৈচিত্র ও অনন্যতা তার বিপরীতধর্মিতার দিকে চলে যায়, এবং সমগ্রতাধর্মী অনুরূপত্ব ও অশেষ পুনরাবৃত্তির ফলে যথার্থ পার্থক্যগুলি মুছে যেতে থাকে।
ইন্দ্রাণীর শৃঙ্খলা ও সাফল্যের কাঠামো ও সমগ্রতার ভিন্ন প্রেকআপটে স্হাপন করেই যেমন অভিজিৎ-অরিন্দমের আকাঙ্খা-উৎপাদনের সিজোফ্রেনিক প্রবাহকে সজ্ঞায়িত করা সম্ভব--- অন্যদিকে তেমনি তাদের এই আকাঙ্খার রাজনীতি ইন্দ্রাণীর উক্ত শৃঙ্খলা ও সাফল্যকেই যথার্থ ও অনিবার্য বলে প্রমাণ করে ফেলে। তার ফলে তাদের আকাঙ্খার রাজনীতি যথাপ্রাপ্ত পরিসরের সিনক্রোনিক বা সমকালীন ব্যাখ্যা দিতে পারে, কিন্তু দীর্ঘ কালগত বিখাশের ডায়াক্রোনিক বা ঐতিহাসিক ধারণার কাঠামো নির্মাণ করতে পারে না।তার পাশাপাশি অতনু-মানসীরা তাদের কর্মকান্ডের সূত্রে অনেক বিশৃঙ্খলা ও সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও--- একদিকে যেমন বিষয়ীর এক ধরনের সুস্হিতির কথা বলে, অন্যদিকে তেমনি তা বিষয়ীর নিজেকে পুনর্নিমাণের ঐতিহাসিক ক্ষমতার প্রতিও গুরুত্ব দেয়। অন্যভাবে বলা যায়, অতনু-মানসীদের আকাঙ্খার রাজনীতি বাইরের শক্তির নিজস্ব উৎপাদন ক্ষমতার অধীন থাকা বিষয়ীকে বিচ্ছিন্ন ও খন্ডায়িত সত্তা হিসেবে দেখার কথা না-বলে--- সামাজিক ও ঐতিহাসিক দ্বারা নির্ধারিত বিষয়ীর কথাও বলে। যে-বিষয়ী আবার অন্য বিষয়ীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে সক্রিয়ভাবে ওই সব বস্তুগত, সামাজিক ও ঐতিহাসিক শক্তিসমূহকে পরিবর্তিত করতে পারে।
মলয়ের উপন্যাসে বিহারের বিভিন্ন জাতের লড়াইতে বাঙালিদের অবস্হা যে কতটা করুণ তা আমরা স্পষ্ট বুঝে নিতে পারি। হয় তাদের বিহারি সংস্কৃতির আধিপত্য মেনে নিতে হবে, নয় তো কলকাতায় চলে আসতে হবে, অথবা ক্রান্তিকারীদের সঙ্গে মিশে যেতে হবে। ১৯৯৫-এর একটি হিসেব থেকে জানা যায়, বিহারের মোট জনসংখ্যার ১১.২ শতাংশ উচ্চবর্ণের, ২১.২ শাতাংশ পিছড়ে বর্গ, ১৮.৫ শতাংশ তপশিলী জাতি, ৭.৭ শতাংশ তপশিলী উপজাতি, ১৪.১ শতাংশ মুসলমান, সব থেকে পিছিয়ে-পড়া জাতি ২৯.৫ শতাংশ ও অন্যান্যরা ১.৮ শতাংশ। হিন্দিভাষী ৮০ শতাংশ, উর্দুভাষী ৯.৯ শতাংশ, বাংলাভাষী ৩.৫ শতাংশ। ভারতবর্ষে দারিদ্রসীমার নিচে বাস করেন ৪০ শতাংশ মানুষ, বিহারে সেখানে ৫৯ শতাংশ। উচ্চবর্ণের মধ্যে রয়েছে ব্রাহ্মণ, ভুমিহার, রাজপুত ও কায়স্হরা। মধ্যবর্ণের মধ্যে যাদব, কৈরি ও কুর্মিদের সংখ্যা সব থেকে বেশি।বর্তমানে ক্ষমতার ভাগ-বাঁটোয়ারাতে যাদবরাই এখন সবথেকে এগিয়ে। ১৯৯০-এর মন্ডল কমিশনের রিপোর্ট সামনে আসার পর থেকে সত্তা পরিবর্তনের যে-প্রক্রিয়ার সূচনা হয়েছিল তাতে কুর্মি গোষ্ঠীও শামিল ছিল। কিন্তু ক্ষমতার ভাগ-বাঁটোয়ারাতে অসন্তুষ্ট হয়ে তারা বিরোধী অবস্হানে চলে যায়, যাদের প্রতিনিধি নিতীশ কুমারের সমতা পার্টি। বিহারে জনতা দল সমাজের মধ্যস্তরের সমর্থনেই ক্ষমতায় আসীন।যাদব উথ্থানে কিন্তু নিম্ন মধ্যবিত্ত, গরিব কৃষক, ভূমিহীন কৃষক, সাধারণ মধ্যবিত্ত, মেহনতি জনতাসহ আর্থিক দিক দিয়ে সার্বিকভাবে পিছিয়ে-পড়া শ্রেণীভুক্ত মানুষদের সামনে ক্ষমতার কেন্দ্রে পৌঁছোনোর কোনও সিঁড়িই উন্মোচিত হয়নি। বিহারে যে-কোনও জাতের মানুষ অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে-পড়া শ্রেণীতে অবস্হান করলেই শোষণ, সামাজিক অন্যায় ও অত্যাচারের শিকার হন। উচ্চবর্ণের স্বার্থ অর্থাৎ কায়েমি স্বার্থে ধাক্কা লাগলেই জাতপাতের দ্বন্দ্ব হিংস্র দাঁত-নখ প্রকাশ করে ফ্যালে প্রকাশ্যে। শ্রেণীস্বার্থ বিঘ্নিত হলে উচ্চবর্ণের মানুষেরা রাষ্ট্র-অর্থ-পেশি ক্ষমতাকে নির্বিচারে প্রয়োগ করে নিম্নবর্ণের মানুষদের হত্যা করে, সমস্ত ধরনের মানবাধিকারকে লঙ্ঘন করে।
পশ্চিমবঙ্গের পরিস্হিতি সেরকম নয় অবশ্যই। রাজনৈতিক সমাজ ও জনসমাজের ভিতরকার কার্যকারণ -সম্পর্ক বিহার ও পশ্চিমবঙ্গে প্রায় বিপরীতধর্মী।বিহারে আজও জাতিদ্বন্দ্বের ভাষা কর্কশ, প্রাক-আধুনিক এবং রাষ্ট্রকে সে-ভাষা আগে নিজের ভাষায় অনুবাদ করে নিয়ে তবে কাজ করতে হয়। পশ্চিমবঙ্গে সুশৃঙ্খল-আধুনিক রাষ্ট্র এটাকে বদলে দিয়ে সমাজ ও গোষ্ঠীর স্বাধীনতার এক্তিয়ারকে খর্ব করে দিয়েছে। এখানে উচ্চবর্ণ, মধ্যবর্ণ ও তপশিলীরা সবাই রাষ্ট্রের ভাষাতেই কথা বলে। আধুনিক কথোপকথনের ক্ষেত্রে প্রধান সোপান হল আধুনিক শিক্ষা। পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষা একসঙ্গে তিনটি উদ্দেশ্য সাধন করছে: ১) জীবিকাগত সাফল্যের চাবিকাঠি হিসেবে; ২)আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্হার মুখোমুখি হয়ে প্রতিষ্ঠা বা সুবিধাজনক অবস্হান তৈরিতে; ৩) গ্রামসমাজে ক্ষমতালাভ করতে পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার সাহায্যে সমাজে কর্তৃত্বের ভূমিকা অর্জন করার গুরুত্ব অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় অনেক বেশি। সেটা বোঝা যায় এটা দেখে যে, অন্যান্য রাজ্যে অব্রাহ্মণ বা 'পশ্চাদপদ'-রা কর্তৃত্বপূর্ণ সামাজিক ভূমিকার জন্য ব্রাহ্মণদের রীতি ও আচারকে অনুকরণ করতে চায়। এই প্রবণতা আর.এস.এস. ও বিজেপির মধ্য ও নিম্ন বর্গের নেতা ও কর্মীদের মধ্যে প্রবলভাবে দৃশ্যমান।পশ্চিমবঙ্গে এই ধরনের সংস্কৃতায়নের প্রভাব প্রায় নেই , এবং তার পাশাপাশি আবার উগ্র পাশ্চাত্য জীবনযাপনের মানসিকতাও বাঙালি সমাজে নিন্দনীয়। তাই সামাজিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে শিক্ষার ভূমিকা এখানে অনেক তাৎপর্যপূর্ণ। শিক্ষার সূত্র ধরেই পশ্চিমবঙ্গের নতুন পঞ্চায়ের ব্যবস্হা ও রাজনৈতিক দলগুলো রাষ্ট্রের অসংখ্য আঙুলের মতো ছড়িয়ে থেকে জনসমাজের ওপর রাজনৈতিক সমাজের মতাদর্শগত আধিপত্যকে নিশ্চিত করেছে। তার ফলেই উচ্চবর্ণ, নিম্নবর্ণ ও মধ্যবর্ণ--- সবাই অতি সহজেই রাষ্ট্রকে গ্রহণ করে। সব বর্ণের সব প্রতিবাদ-পদ্ধতি ও জাত-বিদ্বেষ রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত সীমার মধ্যেই আবদ্ধ থাকে। শিক্ষা ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ-তাঁবেদারির সূত্র ধরে ক্ষমতাবৃদ্ধির বিষয়ে বিভিন্ন জাতির মানুষ মনোযোগী হয়ে উঠেছে। তার ফলে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী ক্রমশ ভোটব্যাংক হিসেবে নিজেদের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছে। তাই তাদের রাজণেতিক সক্রিয়তার সঙ্গে তাদের জাতিসত্ত্বার সম্পর্ক ক্রমাগত ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, স্বাধীনতার পরবর্তীকালে, বিশেষ করে ১৯৭৭-এর পর, পশ্চিমবঙ্গে ভূমিসংস্কার ও চাষের ক্ষেত্রে নতুন প্রযুক্তিকে সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগের পরিণতিতে অনেক স্বয়ম্ভর মাঝারি চাষিই অবস্হাপন্ন জোতদারে পরিণত হয়ে গ্রামীণ রাজনীতির কেন্দ্রস্হলে এসে দাঁড়িয়েছে।
পশ্চিমবঙ্গে এখনও পর্যন্ত আইন মেনেই একজন মানুষ যে পরিমাণ জমি নিজের হাতে রাখতে পারেন, তার ভিত্তিতে তাঁকে জোতদার বলা যায়। লক্ষ করবার বিষয়--- বিত্তশালী, প্রভাবশালী মাঝাতি চাষিদের এই নতুন শ্রেণিটির অধিকাংশই মধ্যশ্রেণি বা জাতির সদস্য। তার পাশাপাশি এটাও লক্ষ করবার বিষয় যে এরা যেসব মজুর ভাড়া করেন তাদের মধ্যে উচ্চ বা মধ্যবর্ণের কাউকে পাওয়া প্রায় অসম্ভব। নতুন ক্ষমতাবান এই মধ্যবর্ণের মানুষদের আয়ের প্রধান উৎস অবশ্যই কৃষি, ব্যবসা ও শিল্প উদ্যোগ।তাঁদের একটি অংশ আবার শিক্ষকতা পেশার সঙ্গে যুক্ত। তাদের প্রকাশক্ষমতা উচ্চ মানের।পঞ্চায়েতের বিভিন্ন স্তরে তাদের প্রতিনিধি আছে। মনে রাখার কথা, ১৯৭৮-এর পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময়ে বিভিন্ন স্তরে প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে ও নির্বাচনের পরে কর্মমর্তা নির্বাচনের সময়ে নিম্নবর্ণের মানুষদের মর্যাদাপূর্ণ অনুপ্রবেশ ও প্রতিনিধিত্ব যে-আলোড়ন তুলেছিল তা এখন স্তিমিত। পঞ্চায়েতের সূত্রে রাজনৈতিক সমাজ যতই জনসমাজকে নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করেছে, 'জ্ঞান' ততই 'ক্ষমতা'র উৎস হিসেবে আরও বেশি-বেশি করে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। জ্ঞানের অভাবেই নিম্নবর্ণকে ১৯৭৮-এর পর আবার ক্ষমতার কেন্দ্র থেকে প্রান্তে ঠেলে দিয়েছে।অন্যদিকে জ্ঞানের সূত্রেই মধ্যবর্ণ ক্ষমতার কেন্দ্রে চলে এসেছে। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও মেডিকাল কলেজ, গ্রামের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে, উচ্চবর্ণের তুলনায় মধ্যবর্ণের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা এখন অনেক বেশি। স্বাভাবিকভাবেই, ১৯৯০তে মন্ডল কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশের পরে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে যে-ব্যাপক জাতি-ভিত্তিক আন্দোলন দেখা গিয়েছিল, তার কোনো প্রভাবই পশ্চিমবঙ্গে দেখা যায়নি। মধ্যবর্ণের উথ্থান আগেই ঘটে গেছে। তবে সবটাই ঘটেছে রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্বকে স্বীকার করে নিয়ে, রাষ্ট্রের ভাষাকে স্বীকার করে নিয়ে, জনসমাজের ওপর রাজনৈতিক সমাজের নিয়ন্ত্রণকে স্বীকার করে নিয়ে।
বদলি হয়ে কলকাতায় চলে আসার পর অরিন্দমের সঙ্গে যোগাযোগ হব তার প্রাক্তন সহকর্মী কয়েন এগজামিনার ও বর্তমান কলকাতা পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টার আদিত্যর সঙ্গে। আদিত্যের সূত্রে মলয়ের মন্তব্য: 'চাকরির এই ক'বছরেই সরকারি অভিজ্ঞতা ওকে মনুষ্যজনোচিত যুক্তিবাদীতে পালটে ফেলেছে।এরকম হলেই বোধ হয় একজন লোক মানুষ থেকে মানব হয়ে যায়। মানবসন্তান। কলকাতা শহরটা দেশভাগের পর মানব উৎপাদনের কারখানা হয়ে গেছে।' ( জলাঞ্জলি পৃ ৫ )।'মনুষ্যজনোচিত যুক্তিবাদী' হয়ে ওঠার সূত্রে 'মানুষ' 'মানব' হয়ে যায় --- এই রূপকের মাধ্যমে মলয় স্বাধীনতার পরে কলকাতা ও তার সংলগ্ন অঞ্চলে 'আধুনিকতা'র বিস্তারের দিকে ও তার চরিত্রের দিকে আঙুল তুলতে চেয়েছেন। এই অঞ্চলে মানুষের চৈতন্যে শাসকশ্রেণির মতাদর্শগত আধিপত্য ্তটাই প্রবল যে, আদিত্যর 'আদর্শ রুণু গুহনিয়োগী নামে আক প্রাক্তন অফিসার' 'জ্যোতি বসুর মতন কর্মজীবী মুখ্যমন্ত্রী ওব্দি রুণু স্যারের কদর করে পদোন্নতির ধাপ একের পর এক এগিয়ে দিয়েছিলেন ওনার দিকে।' (নামগন্ধ ৫ )। 'এ এস আই-এর চাকরিটা ধর্মঠাকুরের পাঠানো। টাকাও আপনা থেকে আসা শুরু করেছে। ধর্মরাজের কৃপায় একদিন না একদিন রুণু গুহনিয়োগীর মতন প্রভাব প্রতিপত্তি লোকবল ঐশ্বর্য সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা আর গণমাধ্যমের আদরযত্ন পাবে। বাসের সিটে বসে হাতজোড় করে আদিত্য। কপালে ঠেকায়।' (নামগন্ধ ৮-৯)।
কলকাতা ও সংলগ্ন অঞ্চলের মধ্যবিত্ত চৈতন্যের সামগ্রিক পণ্যায়নের প্রক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে আদিত্যর ভাবনাকে বোঝা যাবে না। আদিত্যর ভাবনা শুধু একজন পুলিশ কর্মীর ভাবনা নয়। অর্থ ও ক্ষমতার প্রতি এই আকাঙ্খা প্রায় সব পেশার মানুষদের মধ্যেই সংক্রামিত হয়েছে। নৈতিকতার মানও সেই স্তরেই এসে ঠেকেছে। কলকাতা সত্যই মানব উৎপাদনের কারখানায় পরিণত হয়েছে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে আড্ডা দিতে-দিতে অরিন্দম, আদিত্য আর যিশু বিশ্বাসে আলোচনায় দেশভাগ, উদ্বাস্তু আন্দোলন, ট্রাম আন্দোলন, আর এই দুই আন্দোলনের নেতা ভবেশ মন্ডলের কথার মধ্যেই স্বচ্ছন্দে রাইটার্স বিল্ডিংএর সুশ্রী কিশোরী চা-উলির সঙ্গে যিশুর যৌন সম্পর্কের প্রশ্ন এসে যায়। 'হত্যা আর মৃত্যু থেকে যৌনতার এলাকায় খেলাচ্ছলে পৌঁছে উপশম হল অরিন্দমের।' আধুনিকতা মানুষকে প্রকৃতি থেকে ছিঁড়ে আলাদা করে সংস্কৃতিবান বানিয়ে ফেলবার পর তাকে নির্মমতার ওপারে অন্য কোনও মমতাহীনতায় পৌঁছে দিয়েছে। স্পষ্টই টের পাওয়া যাচ্ছে যে আদিত্য পোঁছে গেছে সে জায়গায়। কত সহজে খুনের আতঙ্ক থেকে নিজেকে যৌনতার আমোদে নিয়ে এল।' মিডিয়ার মেসেজও এভাবেই মানুষকে হিংস্রতায় দোলাতে-দোলাতে বিনোদনের জগতে ডুবিয়ে দেয়। ধনতন্ত্র যতই মানুষকে সাম্প্রতিকতম তথ্য-প্রযুক্তির স্রোতে ভাসিয়ে দেয়, বিনোদনের আমোদে ডুবিয়ে দেয়--- সে ততই সমসাময়িকে বাঁচতে শুরু করে, ইতিহাসবোধ হারাতে শুরু করে। এলিয়নেশন ও রিইফিকেশনের বোধ সামাজিক উৎপাদনের ভাবনা থেকে মানুষকে সরিয়ে নিয়ে যায়।পণ্যমোহের স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। ১৯৮০ ও ১৯৯০-এর দশকে কলকাতা ও সংলগ্ন অঞ্চলের মধ্যবিত্ত শ্রেণির রূপান্তর এইসব দার্শনিক ও মনস্তাত্ত্বিক ভাবনাকে সত্য বলে প্রমাণ করেছে। প্র্যাগমাটিজমই এখন গৃহীত মতাদর্শ। সততার মুখোশকে বাঁচিয়ে রাখার সফল কৌশলেরই অন্য নাম সংস্কৃতি। সংস্কৃতিবান প্র্যাগমাটিকরাই এখন কলকাতা ও সংলগ্ন অঞ্চলের মানব।
অরিন্দম যখন কেটলিউলিকে বলে, 'তোমায় আমি বিয়ে করতে চাই', তখন তার জবাবে কেটলিউলি বলে, 'কুটো দিনের জন্য ?' অরিন্দম বোঝে: 'কেটলিউলির মেরুতে বার্তা পৌঁছাবার ভাষা ওর কাছে নেই। হিন্দি আর বাংলা সিনেমা কেটলিউলির কাছে প্রেম-ভালোবাসাকে হাস্যকর আর ফালতু করে দিয়ে থাকবে। প্রেমের সমস্ত অভিব্যক্তিকে ফোঁপরা করে দিয়েছে আধুনিকতা।' (নামগন্ধ ৭১)।পাটনায় পাশের ফ্ল্যাটের সাত বছরের বড় পীনোন্নত মহিলার সঙ্গে প্রেমে ব্যর্থ হওয়া ও তারপরে পাগল হয়ে যাওয়া অরিন্দমের কেটলিউলি সম্পর্কে মনে হয়েছিল, 'মেয়েটির শরীর জুড়ে প্রাচীন নিষাদকুলের নাচ লুকিয়ে আছে যেন, মনে হচ্ছিল অরিন্দমের। চিরপ্রদোষ মাখা শ্যামাঙ্গিনী।...এর প্রাণশক্তির জোরের বখরাটুকু আজীবন চায়, আজীবন চায় অরিন্দম।' (নামগন্ধ ৮১)। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের বাস্তবেও কেন্দ্র আর প্রান্ত মিলতে পারে না। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্মীর সঙ্গে কেটলিউলির মিলনের আগেই মারোয়াড়ি হলদিরামের গাড়ির সঙ্গে অরিন্দমের গাড়ির সংঘর্ষে তাদের মৃত্যু হয়। তখন যিশু বিশ্বাসের প্রশ্ন গভীরভাবে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠৈ: 'যৌনসম্পর্কের শ্রেণীবিভাজন কি সত্যিই মেটানো যায় ?'
যিশু বিশ্বাসের এই প্রশ্ন তার নিজের জীবনেই আবার ফিরে আসে 'নামগন্ধ'-র শেষে। দেশভাগের পরিণতিতে ভবেশ মন্ডল তার ছোট বোন খুশিরানী মন্ডলকে নিয়ে চলে এসেছিল পূর্ববঙ্গ থেকে নাকতলায় যিশু বিশ্বাসের পাড়ায়। তারপরে ইউ সি আর সি, ট্রাম আন্দোলন, উদ্বাস্তু আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক কর্মী ভবেশ হঠাৎ একদিন উধাও হয়ে যায় তার বোনকে নিয়ে। খ্রিস্টান যিশু এম বি এ ডিগ্রি নিয়ে, ব্রিফকেসে ল্যাপটপ নিয়ে, পার্ক স্ট্রিটে কনসালটেনসি ফার্ম খুলে, পেশাগত কারণে হুগলির গ্রামে ঘুরতে-ঘুরতে তিরিশ বছর পরে ভবেশ ও খুশিকে আবিষ্কার করে। 'মোকররি আর চাকরান মিলিয়ে বাহান্ন বিঘে জমি আর এক লাখ কুইন্টাল ক্ষমতাসম্পন্ন হিমঘরের অংশিদার পঁয়ষট্টি বছরের গেরুয়া পোশাক, বাঁহাতের সরু-সরি আঙুল দিয়ে আঁচড়াতে থাকে ধবধবে দাড়ি, কালো ফ্রেম গ্রাম্য বাইফোকাল, বাবরিচুল ভবেশ মন্ডলকে হুগলি জেলার এই প্রত্যন্ত গ্রামে দেখে যতটা স্তম্ভিত হয়েছিল, তার চেয়ে অপ্রত্যাশিত ধাক্কায় নির্বাক আনন্দে ছারখার হয়েছিল যিশুর ভবেশকার বোন খুশিদিকে দেখে।' (নামগন্ধ ১৩ )। 'তিরিশ বছর আগে আরামবাগি প্যাঁচে কংরেসি আলুর দাম হঠাৎ বাড়লে, খাদ্য আন্দোলোনের দিনগুলোয় তুলকালাম করেছিল ভবেশকা।...আর আজ হিমঘরের অংশিদার ভবেশকা, সংরক্ষণের ক্ষমতার দ্বিগুণ আলু ঢুকিয়ে, দু'লাখ কুইন্টাল পচিয়ে, সেই একই হুগলি জেলার চাষিদের ভয়ংকর বিপদে ফেলেও নির্বিকার।' (নামগন্ধ ১৩)। পঞ্চাশ বছর বয়স হয়েছে খুশিরানীর। এখন পর্যন্ত যত জন তাকে বিয়ে করতে চেয়েছে, তাদের কেউ খুন হয়েছে, কেউ জ্যান্ত পুড়ে মারা গেছে। 'আমি খুব অপয়া'। খুশি আসলে পূর্ববঙ্গের মিনহাজুদ্দীন খানের নাতনি খুশবু। ভবেশ দেশ ছাড়ার আগে তাকে শৈশবে তুলে নিয়ে আসে। এদেশে এসে পরিচয় দেয় সৎবোন বলে। সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের পুরোনো খবরের কাগজে খুশির দাদুর দেয়া বিজ্ঞাপনের সূত্রে যিশু একথা জানলেও খুশি জানে না। তাই তার সঙ্গে যারই বিয়ে ঠিক হয়--- তার কেন অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়, তা বোঝে না। খুশির বন্দিত্ব, অসহায়তা, সরলতা ও নারীত্বের যন্ত্রণাকে বাঁচিয়ে রেখে ভবেশ মুসলিম সম্প্রদায়ের ওপর তার আক্রোশ মেটায় কি ?
গ্রামের ক্ষমতার নতুন অধিকারী মধ্যবর্ণের সঙ্গে ১৯৬০-এর দশক থেকে বাম রাজনীতির সম্পর্ক ঘনিষ্ট। কিন্তু তিরিশ বছর পরে ভবেশের সিন্দুক থেকে যিশু আবিষ্কার করে: 'আলুর বন্ডের বই, পাকিস্তানের পুরোনি একশো টাকরা একটা বান্ডিল, পঞ্চাশ সনের হলদে খড়খড়ে পাকিস্তান অবজার্ভার আর দৈনিক আজাদ, দুটো একই মাসের। একটায় ছবিসুদ্ধ বিজ্ঞাপন, লাল কালিতে ঘেরা। লাল শালুর পাক খুলে শতচ্ছিন্ন বইটা, গীতা নয়, লুপ্ত সোভিয়েত দেশে ছাপানো দাস ক্যাপিটাল...।' (নামগন্ধ ১৭)। এই আবিষ্কারের সূত্রে খুশি ও ভবেশের অতীত ও বর্তমান উন্মোচিত হয়।মার্কসের ক্যাপিটাল লাল শালুতে আবৃত হয়ে সিন্দুকে চলে যায়, ও তুলে-আনা মুসলিম নারীকে বন্দি রাখার সূত্রে মুসলিম সমাজের প্রতি পুষে-রাখা ক্রোধের নিবৃত্তি ঘটানো হয়। এই মজতাদর্শগত ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে ১৯৯৯-তে প্রকাশিত এই উপন্যাসের ভবেশ মন্ডল যদি কোনও সামান্যতম ক্ষতির আশঙ্কাতেই ২০০০-এ বামপন্থী শিবির থেকে দক্ষিণপন্থী শিবিরে চলে যায়--- তাহলে তো অবাক হবার কিছু থাকে না।
১৯৭৭-এর পর ক্ষমতার কেন্দ্রে চলে-আসা গ্রামের মধ্যবর্ণের মানুষদের মতাদর্শগত অবস্হান কেমন ? তপশীলী জাতি ও উপজাতির মানুষদের সামনে এমন কোনও চওড়া সিঁড়ি এখনও নির্মিত হয়েছে কি--- যার মধ্যে দিয়ে তারা ক্ষমতার কেন্দ্রে পৌঁছতে পারে ? এই প্রশ্ন দুটির সঙ্গেই সম্পর্কিত থাকে খুশির এই আকাঙ্খা: 'খুশিদি ফিরে যেতে থাকে তিরিশ বছর অতীতের প্রতিবেশী তরুণের শ্রেণি-নিষিদ্ধ সম্পর্কে, অপ্রত্যাবর্তনীয় সময়ে।' খুশো ও যিশু দুজনাই তো এখন প্রৌঢ়। তবুও তারা মিলতে পারে না--- কেন্দ্র ও প্রান্ত মিলতে পারে না বলেই। খুশিকে নিয়ে পালাবার মুহূর্তে যিশু ডাকাত সন্দেহে গণধোলাইতে খুন হয়।
মলয় রায়চৌধুরী তাঁর উপন্যাস তিনটিতে ইউরোপীয় কোডগুলোকে ভাঙতে-ভাঙতে যে আখ্যান নির্মাণ করেছেন--- তাতে তিনি গভীর ভাবে বুঝতে চেয়েছেন তাঁর স্বদেশ ও স্বকালে মানুষের অভিজ্ঞানকে।তাঁর স্বদেশের মানুষেরা নির্মিত হয়ে উঠেছে এক দীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার পরিণতি হিসেবে। প্রতিটি মানুষের চৈতন্যে ধৃত রয়েছে অসংখ্য উপাদান। এই সব উপাদানের কিছি প্রাকঔপনিবেশিক, কিছু ঔপনিবেশিক আবার কিছু উপনিবেশিকোত্তর চরিত্রের। মলয়ের সমালোচনার লক্ষ্য চৈতন্যের ঔপনিবেশিকিকরণের প্রক্রিয়াকে চিহ্ণিত করা, ঔপনিবেশিক বীক্ষাকে প্রত্যাখ্যান করা। উপন্যাস তিনটিতে একই চরিত্রেরা অনেক সময়েই ফিরে আসে, আবার অনেক চরিত্র একবার দেখা দিয়েই হারিয়ে যায়। উপন্যাস তিনটিতে ঔপনিবেশিক সংস্কারকে মেনে নিয়ে একটি চরিত্রকে নায়ক বানিয়ে, একক কন্ঠস্বরের শাসনকে প্রতিষ্ঠা করে, প্রথাগত ট্রিলজি লিখবার প্রয়াস নেই। যদিও তা করবার সুযোগ অবশ্যই ছিল।অরিন্দমকে মাঝখানে রেখে তা করাই যেত। কিন্তু মলয় সচেতনভাবে এই ঔপনিবেশিক আদরাকে ভেঙে কন্ঠস্বরের প্রাচুর্যের সূত্রে নতুন ধরনের দ্বিবাচনিকতার জন্ম দিয়েছেন। বিহার ও পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক সমাজ ও জনসমাজের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিন্নতাকে মলয় যেভাবে উন্মোচন করেছেন তা ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে ইতিহাসের একরৈখিকতাকে অপ্রমাণ করেছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসই যদি একরৈখিক না হয়, তাহলে বিশ্ব ইতিহাসের একরৈখিকতাকেও প্রমাণ করা যায় না। তাহলে ঔপনিবেশিক শাসনের যথার্থতাকেও প্রমাণ করা যায় না। আর তা যদি করা না যায়, তাহলে তৃতীয় বিশ্বের নিজস্ব জ্ঞানতত্ত্ব ও নন্দনতত্ত্বের প্রয়োজনও অস্বীকার করা যায় না।
যাঁরা মনে করেন ইউরোপ ইতিহাস নির্মাণ করে ও তৃতীয় বিশ্ব হচ্ছে ইতিহাসের কাঁচামাল, মলয়ের উপন্যাস তিনটি তাঁদের ধারনার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ। মলয় দেখান ভারতবর্ষ মানেই উচ্ছিষ্ট-উপনিবেশ নয়, বিশৃঙ্খল-গরিব-হাঘরে-অলস-ট্রাইবাল নয়। তা দেখাতে গিয়ে মলয়কে নির্মাণ করে নিতে হয়েছে এক নিজস্ব ভাষাকাঠামো যা তিনটি উপন্যাসে একইরকম নয়। ভারতীয় বাস্তবে বিভিন্ন রাজ্যের ভিন্নতা এই ভাষাকাঠামোর ভিন্নতাকে অনিবার্য করে তোলে না কী ? শাসকশ্রেণি তার মতাদর্শগত আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেই তার প্রতিক্রিয়া হিসেবে অনিবার্য হয়ে উঠে আসে প্রতিরোধের ভাষা--- বিকল্প সন্দর্ভ। মলয়ের তিনটি উপন্যাস জুড়ে এই সন্দর্ভের পার্ধক্য সম্পর্কে বারবার সচেতন করা হয়েছে পাঠককে। বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের বাস্তবে, ভাষাতাত্ত্বিক সন্দর্ভ নির্মাণে, তার জন্য ভিন্ন-ভিন্ন আখ্যান কৌশল অবলম্বন করেছেন মলয়। আবৃত্তিকার, সংবাদ পাঠক-পাঠিকা, এফ এম তরঙ্গের অনুষ্ঠানে সঞ্চালকদের কৃত্রিম উচ্চারণ বাংলা ভাষায়, বিভিন্ন অঞ্চলের, উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য, সূক্ষ্মতা, সৌকর্যকে যেভাবে বিনষ্ট করেছে, তার বিরুদ্ধে মলয়ের উপন্যাস তিনটিতে সচেতনভাবে প্রতিরোধ প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়--- সচেতন ভাষাগত নির্মাণের সূত্রে। আর এই নির্মাণের সূত্রেই মলয় পাশ্চাত্য মানদন্ডের বাইরে চলে আসার প্রয়াস পান।
আমাদের সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত প্রতিষ্ঠানগুলো ধারাবাহিকভাবে পাশ্চাত্য মানদন্ডগুলোকেই একমাত্র মানদন্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পেয়েছে মহাসন্দর্ভের সাহায্যে। মলয়ের উপন্যাস তিনটিতে তাই বারবার প্রান্তে দাঁড়িয়ে জনসমাজের গভীরে প্রবেশের চেষ্টা চালাতে-চালাতে, প্রতিষ্ঠান-স্বীকৃত মানদন্ডগুলোকে প্রত্যাখ্যানের প্রয়াস খুঁজে পাওয়া কষ্টকর নয়। আর এই প্রয়াসকে বাদ দেওয়া মলয়ের পক্ষে সম্ভব ছিল না। যে কোনও সৎ শিল্পীর মতো মলয়ও তাঁর বাস্তবের স্বদেশে সংখ্যালঘু, বিপর্যস্ত। তাই তাঁর কল্পিত স্বদেশে তিনি বার বার অতিক্রম করে যেতে চান কেন্দ্র ও প্রান্তের অলঙ্ঘনীয় দূরত্বকে।ঔপনিবেশিকতা-মুক্ত জনসমাজই মলয়ের শেষ আশ্রয় বলেই 'নামগন্ধ' উপন্যাসের শেষে খুশিরানী মন্ডলের শেঢ় গন্তব্যের হদিশ তিনি দেন না। তিনি জানেন খুশিরানীকে সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় অনুসন্ধান করতে হবে, নির্মাণ করতে হবে তার স্বদেশের ইতিহাসকে, তার আত্মপরিচয়কে।
 পল ভেরলেন | 122.179.172.247 | ২৪ আগস্ট ২০২১ ১৯:২৫734899
পল ভেরলেন | 122.179.172.247 | ২৪ আগস্ট ২০২১ ১৯:২৫734899পল ভেরলেন ও তাঁর কবিতা
যদিও শেষ জীবনে, ১৮৯৬ সালে যখন তাঁর মৃত্যু হল, তাঁকে ‘গুরু’র শিরোপা দিয়েছিলেন তাঁর বন্ধু ও অনুরাগিরা, ফরাসি কবি পল ভেরলেনের সঙ্গে জনসাধারণের সম্পর্ক সারা জীবন ধরে বেশ ওতোর-চড়াও দিয়ে গিয়েছিল । আঁর সাহিত্যিক খ্যাতি ক্রমশ অপকর্ষের পথে গিয়ে আবার ফিরে এসেছিল, যখন প্যারিস শহরের অসংখ্য মানুষ তাঁকে ‘কবিদের রাজকুমার’ তকমায় ভূষিত করে মৃত্যুর তিনদিন পর তাঁর শবানুগমন করেছিলেন । জীবদ্দশায় তাঁর খ্যাতি ক্ষতিগ্রস্ত হবার প্রধান কারণ তাঁর মর্মপীড়াদায়ক আচরণ, অথচ তখন তিনি প্রতীকবাদী কবিতা আন্দোলনকে প্রভাবকারী একজন গুরুত্বপূর্ণ কবি হিসাবে স্বীকৃতি পেয়ে গেছেন । উনিশ শতকের সত্তর দশকে ‘ডেকাডেন্ট’ আন্দোলনের আদর্শ কবি হিসাবে তখন তিনি প্রতিষ্ঠিত । তাঁর সাহিত্যপ্রতিভার কারণে যতোটা ততোটাই তাঁর খ্যাতির ভিত্তি তাঁর চেয়ে বয়সে অনেক ছোট তরুণ কবি আর্তুর র্যাঁবোর সঙ্গে যৌনসম্পর্কের উথালপাথালের ও আবসাঁথ টেনে মাতাল থাকার দরুণ ।
উত্তর ফ্রান্সে ৩০ মার্চ ১৮৪৪ সালে পল ভেরলেনের জন্ম ; তিনি ছিলেন সেনাবাহিনির ক্যাপ্টেন নিকোলাস ও আরাসের জনেক কৃষকের মেয়ে স্তাফানি দেহির সন্তান । নিকোলাস ছিলেন কঠোর প্রকৃতির, কিন্তু তাঁর মা পলকে বাবার ক্রোধ থেকে আগলে রাখতেন । বাবা-মায়ের বিয়ের তারো বছর পর জন্মেছিলেন পল ; স্বাস্হ্য খারাপ হবার কারণে তাঁর মায়ের গর্ভপাত হয়ে যেতো বা মরা অবস্হায় বাচ্চা জন্মাতো । ১৮৫১ সালে সেনাবাহিনি থেকে পদত্যাগ করে নিকোলাস প্যারিসে চলে যান ; সেখানে পল সঙ্গী হিসাবে পান এলিজা মোনকোম্বলে নামে তাঁর অনাথ খুড়তুতো বোনকে, যার প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন বয়ঃসন্ধির রসায়নে । পলকে স্কুলে ভর্তি করা হয় । যতো তাঁর বয়স বাড়তে থাকে ততোই প্রকাশ পেতে থাকে তাঁর ক্রোধের দমক । পল ভেরলেনের বয়ঃসন্ধিকাল থেকেই কবির কন্ঠস্বর লালিত হতে থাকে । সংবেদনের অস্হিরতা থেকে প্রথম দিকের কবিতায় তিনি জগত থেকে পালাবার কথা লিখেছিলেন : ভয়হীন স্বপ্নদ্রষ্টার জন্য তোমার ডানা মেলে ধরো,/আর তাকে উড়িয়ে নিয়ে যাও !/বিদ্যুৎ, আমাকে নিয়ে যাও !
তাঁর আত্মা পরমের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছে, এমন কল্পনায় নিজেকে চুবিয়ে তিনি জগতকে প্রশ্ন করা আরম্ভ করলেন এবং নিজের সৃষ্ট জগতকে তুলে ধরলেন তার বিপরীতে । সাধারন মানের ছাত্র, তাঁর প্রধান আগ্রহ ছিল কবিতা লেখায় এবং প্যারিসে তিনি আইন-শিক্ষার চেয়ে, যে কলেজে তাঁর বাবা ভর্তি করে দিয়েছিলেন, লাতিন কোয়ার্টারে বেশি সময় কাটাতেন। ১৮৬৩ সালে প্রকাশিত হলো তাঁর প্রথম সনেট ‘মঁসিয় প্রুধোম’ । ছেলে লেখালিখি করে বেয়াড়া হয়ে যাচ্ছে আঁচ করে তাঁর বাবা তাঁকে মেয়রের দপ্তরে চাকুরিতে ঢুকিয়ে দিলেন । কাজের পর সন্ধ্যায় ভেরলেন কবিদের আড্ডায় যাতায়াত আরম্ভ করলেন, বিশেষ করে থিওদোর দ্য বাঁভিলের কাছে, কবিতার সাম্প্রতিক টেকনিক সম্পর্কে আলোচনার জন্য । কিন্তু আশঙ্কা ও আশার পরস্পরবিরোধী মানসিকতায় আক্রান্ত হয়ে বিষাদে ভুগতেন ভেরলেন । কেবল কবিতায় পেতেন সাময়িক শান্তি । ১৮৬৬ সালে তিনি প্রথম কবিতা সংকলন প্রকাশ করলেন ‘শনির কবিতা’ ( Poemes saturniens ) শিরোনামে । বইয়ের নামকরণ করেছিলেন শার্ল বোদলেয়ারের ‘ক্লেদজ কুসুম’ ( Les Fleurs du mal, 1857 ) বইয়ের একটি কবিতার প্রভাবে কিন্তু নিজের শৈলী গড়ার বদলে কবিতাগুলো ছিল বাঁভিল আর ভিক্তর উগোর অনুকরণ। বইটির অধিকাংশ কবিতা উৎসর্গ করেছিলেন খুড়তুতো বোন এলিজা মোনকোম্বলেকে, যাকে তিনি গোপনে ভালোবাসতেন । নিজের কাজের প্রতি বোদলেয়ারের অনাসক্তির প্রশংসা করলেও, ভেরলেন নিজের লেখালিখির সঙ্গে সম্পূর্ণ প্রলিপ্ত ছিলেন । ‘শনির কবিতা’ বইয়ের কবিতাগুলির কেন্দ্রে ছিল প্রেম ও কামেচ্ছা । এর পরই ১৮৬৯ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর কাব্যগ্রন্হ ‘দুরন্ত উৎসব’ ( Fetes galantes ) যার অধিকাংশ কবিতায় আছে চাঁদের চিত্রকল্প ; ভুতুড়ে গ্রামে প্রেতেদের নাচ ; মিলিয়ে যেতে-থাকা স্বর্গোদ্যানের বিষাদময় বাগানে ফোয়ারা ঘিরে সঙদের আর ঘুঘুদের চরকি, লাফ আর নাচ । ভেরলেন প্রয়াস করেছিলেন আঠারো শতকের চিত্রকর আঁতোয়া ওয়াত্তেউয় ও জঁ-অঁরে ফ্রাগোনার উপস্হাপনাকে কবিতায় ধরে রাখতে, এবং সেই সঙ্গে ওয়ালটার পাতের, উগো, জেরার দ্য নেরভাল, থিয়োফিল গতিয়ে, ইতালিয় কমেদিয়া দেল-আরতে থেকে সূত্র আহরণ করতে । কিন্তু এই কাব্যগ্রন্হের পাঠক তিনি পাননি ; বইটা ছিল বিপর্যয় । তাঁর আবসাঁথ খাবার পরিমাণ বেড়ে গেল এই বিপর্যয়ে ।
কয়েকমাস পরে তাঁর পরিচয় হয় ম্যাথিলে মত নামে বয়সে বেশ ছোটো তরুণীর সঙ্গে এবং গভীর প্রেমে পড়েন । ১৮৭০ সালে প্রকাশিত পরের কাব্যগ্রন্হ ‘ভালো গান’ ( La bonne chanson ) উৎসর্গ করলেন তাঁকে । এই কাব্যগ্রন্হের প্রকাশভঙ্গী অনেক সরাসরি ; প্রতিফলিত হয়েছে জীবনকে নিয়ন্ত্রন করার ও মানসিক শান্তি পাবার চেষ্টা -- জীবনের বাস্তবতা সম্পর্কে তাঁর ধারণা হয়ে গিয়েছিল এবং মানসিক শুদ্ধতার জন্য আকুল আকাঙ্খা দেখা দিয়েছিল । কবিতাগুলো দ্রুত লিখেছিলেন ভেরলেন এবং তার অধিকাংশই তিনি ম্যাথিলেকে প্রথম দেখার পর লিখে পাঠিয়েছিলেন । তাঁদের পরিচয়ের পরে-পরেই, প্রেমিক-প্রেমিকার চাপে, তাঁদের বিয়ে হয়, এবং ছয় মাস ভালোই কেটেছিল কিন্তু আর্তুর র্যাঁবো নামের এক কবি যশোপ্রার্থীর প্রতি তাঁর টান সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে দ্যায় ।
১৮৭১ সালে ভেরলেনের সঙ্গে র্যাঁবোর দেখা হয়, র্যাঁবো তাঁকে তাঁর ‘মত্ত নৌকো’ ( Le Bateau ivre ) কবিতাটি পড়ে শোনান । ভেরলেনের সঙ্গে র্যাঁবো যোগাযোগ করেছিলেন চিঠি লিখে, আর ভেরলেন তাঁকে তাঁর পরিবারে অতিথি হিসাবে থাকার আমন্ত্রণ জানান । অবিচ্ছেদ্য হয়ে দাঁড়াল তাঁদের পরস্পরের সম্পর্ক । ইতিমধ্যে ভাঙন দেখা দিলো ভেরলেন আর তাঁর স্ত্রীর সম্পর্কে ; র্যাঁবোর আচরণ সমালোচনা করার কারণে ভেরলেন স্ত্রীর গায়ে হাত তুললেন । এই সময়ে র্যাঁবোর অশহুরে চাষাড়ে আচরণ আর তাঁদের দুজনের যৌনসম্পর্কে প্যারিসে সাহিত্যিক মহলে ছড়িয়ে পড়েছিল । ১৮৭১ সালের অক্টোবরে ম্যাথিলদের ছেলে জর্জের জন্ম হল । কয়েকমাস পরে ভেরলেন আর র্যাঁবো প্রথমে বেলজিয়াম আর সেখান থেকে ইংল্যাণ্ডে পাড়ি মারলেন । ম্যাথিলদে বিবাহবিচ্ছেদের আবেদন করতে বাধ্য হলেন ।
পরের তিন বছর ভেরলেন ও র্যাঁবো, প্রেমিক-প্রেমিকার মতন জুটি বেঁধে, লণ্ডন, ব্রুসেলস ও প্যারিস শহরগুলোয় ঘুরে-বেড়িয়ে কাটালেন । ১৮৭২ আর ১৮৭৩ সালের মাঝে দুই প্রেমাসক্তের মাঝে অনেকবার ছাড়াছাড়ি আর পুনর্মিলন হল, আর শেষ পর্যন্ত ব্রুসেলসে দুজনের কথা কাটাকাটির পর ভেরলেন র্যাঁবোকে পিস্তল দিয়ে গুলি করে আহত করলেন আর আঠারো মাসের জন্য জেলে গেলেন । জেলে তিনি ক্যাথলিক খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা নিয়ে ঈশ্বরবিশ্বাসী হতে চাইলেন ।
মার্চ ১৮৭৪ সালে প্রকাশিত হল ভেরলেনের কাব্যগ্রন্হ ‘শব্দহীন রোমান্স’ ( Romances sans paroles ) বেলজিয়াম ও ইংল্যাণ্ডে লেখা একুশটি কবিতা সংকলিত করে। প্রথম কয়েকটা কপি ভেরলেন জেলে বসে পেয়েছিলেন, এবং বইটা তিনি উৎসর্গ করেছিলেন র্যাঁবোকে, কিন্তু তা তাঁর বিপক্ষকে প্ররোচিত করবে, উকিলের এই পরামর্শে, র্যাঁবোর নাম বাদ দিয়ে দ্যান । ‘ভুলে-যাওয়া গান’ ( Ariettes oubliees ) কবিতাটিতে ধরা যায় ভেরলেনের স্বরভঙ্গীর পরিবর্তন ; কবি পরিচিত, সাঙ্কেতিক, স্মৃতিবেদনাতুর কন্ঠে তাঁর পাঠকদের কাছে স্বীকৃতি দিচ্ছেন । র্যাঁবোর প্রভাবে ভেরলেন আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন শব্দের জীবন-বদলকারী ক্ষমতা । তাঁরা দুজনে যখন বেলজিয়ামে ছিলেন তখনকার কবিতায় যাত্রাপথে কবির কামুক অ্যাডভেঞ্চার উদ্ঘাটিত হয়, তাই ‘ওয়ালকোর্ট’ কবিতায় তিনি লেখেন :
ইঁঁট আর টালির সারি,
ওহ, কমনীয় আবরক
আরামপ্রদ আশ্রয়
প্রেমীদের জন্য
……………...
কাছেই রেলস্টেশন
সমকামের পথ বেছে নেওয়ার
এখানে কোন ঝড়ো হাওয়া,
শুভ পর্যটক ইহুদিরা ?)
উপরোক্ত বইয়ের কিছু কবিতায় ধরা পড়ে ম্যাথিলদের প্রতি পাল্টা-অভিযোগ আর অসুখি বিয়ের জন্য ভেরলেনের অপরাধবোধ । বইটি প্রকাশের এক বছর পর জেল থেকে ছাড়া পেয়ে তিনি লণ্ডনে গিয়ে ফরাসি শিক্ষকের চাকরিতে যোগ দেন । ১৮৭৯ সালে সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য প্যারিস ফিরে তিনি আবার ইংল্যাণ্ড ফেরেন, নতুন সমকামী তরুণ লুসিয়েন লেতিনোসকে সঙ্গে নিয়ে । এক বছর পর প্যারিস ফিরলে তাঁর মা তাঁকে উত্তর ফ্রান্সে চাষের জমি কিনে দ্যান । চাষবাস জলাঞ্জলি দিয়ে দুজনে প্রেমে আর আবসাঁথ খাওয়ায় এতো মশগুল হয়ে পড়েন যে দেনার দায়ে জমজমা বিক্রি করে দিতে হয় ।
ডিসেম্বর ১৮৮০ সালে প্রকাশিত হয় ভেরলেনের কবিতা সংকলন ‘জ্ঞান’ ( Sagesse ), কিন্তু পাঠক সমাদর পায়নি । পরবর্তীকালে এই বইটিকে বলা হয়েছে ফরাসি কবিতায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান । লাম্পট্যের জীবন থেকে বেরিয়ে এসে এবং র্যাঁবোর জীবনদর্শন প্রত্যাখ্যান করে ভেরলেন তাঁর অন্তরজগতের টানাপোড়েন ও গ্লানিকে আনতে চেয়েছেন বইটির চল্লিশটি কবিতায় । নতুন বাস্তবতার সামনে তিনি বুঝে উঠতে পারলেন যে তিনি একা ও ক্ষয়িত । দশ বছর আগে ফেলে যাওয়া সাহিত্য জগতের সঙ্গে আবার যোগাযোগের চেষ্টা করলেন প্যারিসে ফিরে । কেরানির যে কাজ ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন তা ফিরে পেতে চাইলেন । কিন্তু কেউই তাঁকে চিনতে চাইল না । কয়েকজন বন্ধু তাঁর আর্থিক দুরাবস্হা দেখে বিভিন্ন পত্রিকায় লেখার ব্যবস্হা করে দিলেন । ১৮৮৩ সালে লেতিনোইস মারা গেল টাইফয়েড রোগে । ভেরলেন ভেঙে পড়লেন একেবারে । পথে ও কাফেতে তাঁর মাতলামি অসহ্য হয়ে উঠল অনেকের কাছে ; তাঁকে পুলিশের হুঁশিয়ারিও দেয়া হল ।
ম্যাথিলদের সঙ্গে আইনত বিবাহবিচ্ছেদের কয়েক মাস আগে ১৮৮৪ সালে প্রকাশিত হল ভেরলেনের ‘সম্প্রতি ও পূর্বে’ ( Jadis et naguere ) কাব্যগ্রন্হ । কবিতাগুলো তাড়াতাড়ি একত্রিত করে বইটি প্রকাশ করেছিলেন থাকা-খাওয়ার টাকাকড়ি রোজগারের আর খ্যাতি বজায় রাখার জন্য । Le Chat Noir পত্রিকায় ১৮৮৩ সালে প্রকাশিত তাঁর সনেট ‘অবসন্নতা’ ( Langueur ) ডেকাডেন্ট কবিদের মহলে ‘শ্রেষ্ঠ কাব্যিক শিল্প’ হিসাবে ঘোষিত হয়েছিল। উনিশ শতকের শেষে আর বিশ শতকের প্রথম দিকে গড়ে ওঠা ডেকাডেন্ট কবিদের মতে প্রকৃতির চেয়ে শিল্প উচ্চতর এবং অসীম সৌন্দর্য পাওয়া যাবে মরণাপন্ন ও ক্ষীয়মান বস্তুতে । তাঁরা তখনকার প্রচলিত নৈতিক, নীতিমূলক ও সামাজিক মানদণ্ডের বিরোধী ছিলেন । ভেরলেনের খ্যাতিবৃদ্ধিতে অবদান ছিল জোরিস-কার্ল হুইসমাঁস-এর, যিনি ১৮৮৪ সালে প্রকাশিত তাঁর ‘প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে’ ( A rebours ) উপন্যাসে ভেরলেনের কবিতায় “অস্পষ্ট ও সুস্বাদু বিশ্বাসের” ( vagues et delicieuses confidences ) প্রশংসা করেছিলেন । ভেরলেন অবশ্য তাঁর কবিতাকে এই শৈলী থেকে মুক্ত করে নিবেছিলেন এবং হুইসমাঁস-এর বক্তব্য ভেরলেনের ‘জ্ঞান’ ( Sagesse ) কাব্যগ্রন্হের শেষ কয়েকটি কবিতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ।
১৮৮৬ সালে তাঁর মায়ের মৃত্যুতে ভেরলেন মানসিক ও আর্থিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন । তারপর আর উঠে দাঁড়াতে পারেননি । সেই বছরই প্রকাশিত হয় র্যাঁবোর কাব্যগ্রন্হ ‘ইল্যুমিনেশানস’ , ভেরলেনের লেখা মুখবন্ধসহ ; পাণ্ডুলিপি তিনিই সাজিয়েছিলেন, কেননা র্যাঁবো তখন সাহিত্যজগত ছেড়ে জন্য চলে গেছেন আফ্রিকায় । ভেরলেনের স্বাস্হ্য দ্রুত ভেঙে পড়ছিল, টাকাকড়ি আর আশ্রয়েরও প্রয়োজন ছিল । তিনি ১৮৮৮ সালে প্রকাশ করলেন ‘প্রেম’ ( Amour ) নামের কাব্যগ্রন্হ । পাঠক আর সমালোচকদের মধ্যে সাড়া জাগাতে পারলো না বইটা, যদিও বইটা পেয়ে বাঁভিল তাঁকে উৎসাহিত করার জন্য একটা চিঠি লিখেছিলেন ।
অত্যন্ত গরিব হয়ে গিয়েছিলেন ভেরলেন । প্রচুর আবসাঁথ টেনে মাতাল থাকতেন । প্যারিসের সাহিত্য সভায় কবিতাপাঠ ও বক্তৃতার ডাক পেলে যেতেন ; কিন্তু আশ্রয়ের জন্য দ্বারস্হ হলেন দুই বয়স্ক বেশ্যার, তাদের একজন বিধবা । তাদের মন যুগিয়ে চলার জন্য কবিতা লিখতেন যা নিয়ে দুই বেশ্যার ঝগড়াঝাঁটি তাঁকে আরও বদনাম করত । বদনামের দরুণ অন্তত লোকে তাঁর কবিতার প্রতি আকৃষ্ট হল এবং আগেকার বইগুলো পাঠকরা পড়তে চাইলেন । ১৮৮৯ সালে ভেরলেন প্রকাশ করলেন কামদ ও ধার্মিক কবিতার সংকলন ‘সমান্তরতা’ ( Parallelement ) । কাব্যগ্রন্হটিতে তিনি তাঁর লাম্পট্যের জীবনের সঙ্গে তুলনা করলেন নিরীহ ধার্মিক জীবনের । ১৮৯১ সালে, যে-বছর র্যাঁবো মারা যান, ভেরলেন প্রকাশ করলেন ‘আনন্দ’ ( Bonheur ) নামের কবিতা সংকলন, যাতে তিনি একত্রিত করেছিলেন বিভিন্ন পত্রিকায় চার বছর যাবত লেখা কবিতা । তাঁর আগের কাব্যগ্রন্হগুলোর তুলনায় এই বইটিতে নানা আবেগের কবিতা ছিল ; ধার্মিক কবিতার পাশাপাশি ম্যাথিলদেকে অপমান করে লেখা কবিতা । সেই বছরই প্রকাশিত হল তাঁর কাব্যগ্রন্হ ‘তার জন্য গান’ ( Chansons pour elle ), যে বেশ্যাটি তাঁকে ভালোবাসতো আর খাওয়া-থাকার ভার নিয়েছিল, তাকে উদ্দেশ্য করে লেখা কবিতার সংকলন, তাতে ভেরলেন বলেছেন, “আমাদের পরোয়া করার দরকার নেই আর কলঙ্কজনক হওয়া যাক”, তখন ভেরলেন দুস্হ অবস্হায় জীবনের শেষ প্রান্তে ।
১৮৯২-১৮৯৩ সালে ভেরলেন অত্যন্ত অসুস্হ এবং সব সময়ে আবসাঁথ টেনে মাতাল, কয়েক মাস হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন । ততদিনে তিনি ফরাসিভাষার একজন গুরুত্বপূর্ণ কবি হিসাবে খ্যাত । ইউরোপের বিভিন্ন শহর থেকে কবিতা পাঠের জন্য তাঁকে ডাকা হলেও, স্বাস্হ্যের কারণে কোথাও যেতে পারেননি । প্যারিসেও, তিনি কয়েকটা সাহিত্য সভায় বক্তৃতা দিতে চাইলেও, এতো বেশি মাতাল থাকতেন যে কথা জড়িয়ে যেতো । ১৯৮৪ সালে ভেরলেন প্রকাশ করলেন ‘অঙ্গেপ্রত্যঙ্গে’ ( Dans les limbes ), এবং লিখলেন যে লেখালিখির জন্য তিনি আর কোনও উৎসাহ পান না । মৃত্যুর আগে, ১৮৯৪ সালে তিনি আরেকটি কবিতার বই প্রকাশ করেন ‘শ্লেষ’ ( Epigrammes ) এবং আরও দুটি বইয়ের পাণ্ডুলিপি তৈরি করে যান, ‘মাংস, ১৮৯৬ ( Chair ) ও ‘আক্রমণমূলক’, ১৮৯৬ ( Invectives ) । ১৮৯৫ সালের ৮ই জানুয়ারি মারা যান ভেরলেন । মৃত্যুর কয়েকদিন আগে শেষ কবিতা ‘মৃত্যু’ ( Mort ) প্রকাশিত হয়েছিল । ভেরলেন জেনে যেতে পারেননি যে প্যারিসের তিন হাজার মানুষ তাঁর শবযাত্রায় অংশ নিয়েছিল ।
ঘাসের ওপরে
“এলোমেলো চিন্তা করেন মঠাধ্যক্ষ” -- “আপনি, মারকুইস,
আপনি কি আপনার পরচুলা তেরছা করে পরেছেন,”--
সাইপ্রাসের এই মদ আমাকে কম
জাগায়, তোমার চোখের চেয়ে, ওগো কামারগো !”
“আমার আবেগ” -- “দো, মি, সোল, লা, সি”--
“মঠাধ্যাক্ষ, আপনার শত্রুতা ফাঁস হয়ে গেছে”--
“মেসদামেস, আমি ওই গাছে চড়ি
আর এক নক্ষত্র পেড়ে আনি, ঘোষণা করছি সেকথা ।”
“যে যার নিজের নারীকে চুমু খাক, তারপর
অন্যদের ।” -- “আমিও তাই হতুম, যদি,
কোলের কুকুর !”--- আলতো করে, মহাশয়গণ !”--
“দো, মি ।” -- “চাঁদ !”-- ওহে, কেমন আছো ?”
গলিপথ
ভেড়া চরানোর দিনে যেমন পাউডার আর রুজ মেখেছিল,
বড়ো রিবন ফিতে বেঁধে মেয়েটির কোমলতা,
গলিপথের ছায়ায় , যেখানে সবুজ জন্মায়
বসবার পুরোনো জায়গায় শ্যাওলাধরা, মেয়েটি এঁকেবেঁকে এগোয়
মিনমিনে লাবণ্য আর ভান-করা গোমরে
যেমন আদরের পোষা টিয়াপাখি প্রায়ই করে
মেয়েটির দীর্ঘ গাউন আর তার নীল চাদর ; হাতপাখা
আঙটি-পরা সরু আঙুলে ছড়িয়ে
প্রেমের দৃশ্যে আনন্দিত, প্রায়ান্ধকার
মতামত, ইতউতি তাকাবার সময়ে চোখে হাসি ফুটে ওঠে ।
শ্বেতাঙ্গিনী ; টিকোলো নাক ; মোটার ধাত, টুকটুকে ঠোঁট, ঐশ্বরিক
অবচেতনে গর্বিনী । -- নিগূঢ়, নিঃসন্দেহে,
মাছির মতন রেখাঙ্কিত করা
চোখের বোকা ঔজ্বল্য ।
পদচারণায়
দুধেল আকাশ, অস্পষ্ট, ছিপছিপে গাছের সারি,
মনে হয় হাসছে আমাদের হালকা পোশাক দেখে,--
আমাদের মসলিন আড়ালের উড়াল যেন ডানার
ভঙ্গী, আমাদের সাটিন মৃদু বাতাসে পাখনা নাড়ায় ।
আর শ্বেতপাথরের বাটিতে ঢেউরা আলো খেলায়
আর বীথিপথের বাতাপিলেবুর গাছের ভেতর দিয়ে
নীলাভ হয়ে সূর্যের সোনালী ছেঁকে আসে আমাদের কাছে
আর মৃতপ্রায়, কোনো স্বপ্নের সূর্যালোকের মতন ।
উৎসাহী ফাঁসুড়ে আর প্রতারকদের হৃদয়
কোমলতায় বিরল, কিন্তু যৎসামান্য সঙ্কল্পে বাঁধা,
আমরা প্রতিদিন ফুলঝাড়ের তলায় আনন্দ করি
আর প্রেমিক-প্রেমিকারা মেলায় খেলাচ্ছলে ভিড় করে ।
পাওয়ার পর, ওরা কি সীমা অতিক্রম করবে,
অসম্ভব ছোটো হাত থেকে এক মুঠো খাবার
যখন তারা বীরের জানু নত করে
সবচেয়ে ছোটো আঙুলকে চুমু খাবার ।
আর যেহেতু এটা আপত্তিকর স্বাধীনতা,
এক শীতল চাউনি সাহসী পাণিপ্রার্থীর পুরস্কার,--
অবজ্ঞায় তার ততোটা ছাপিয়ে ওঠে না
রক্তবর্ণ মুখের ভরসাজনক আশ্বাস ।
বন্যপ্রাণী
পোড়ামাটির এক প্রাচীন গ্রাম্যদেবতা,
সবুজের মাঝে এক ঝলক হাসি,
বাগান থেকে আমাদের দেখে ঠোঁট ওলটায়,
গোপন আর ব্যাঙ্গাত্মক হাবভাবে ।
ভাগ্যবশত, ও আগেই জেনে যায়,
প্রিয় মুহূর্তগুলোর অসুখি সমাপ্তি
যা মহানন্দের সঙ্গীত আর হালকা নাচে
আমাদের, চিন্তামগ্ন তীর্থযাত্রীদের নিয়ে এসেছে, এইখানে।
পৃথিবীর ভালোবাসা
সেদিন রাতে বাতাস ভাসিয়েছিল প্রেম
বাগানের প্রায়ান্ধকার কোনে
মৃদু হাসি হাসতো, নিজের বাঁক নামিয়ে
আর যাকে দেখে আমরা হতুম অভিভূত
একদিন ! অন্য রাতের বাতাস ভাসিয়ে দিল ওকে !
সকালের হাওয়ায় শ্বেতপাথরের গুঁড়োর ঘুর্নিপাক ।
ওহ, মন খারাপ হয়ে যায় দেখে, বীথিসারির আড়াল,
ওইখানে বেদির ওপরে, পরিচিত খ্যাতির নাম !
ওহ, মন খারাপ হয়ে যায় ফাঁকা বেদি দেখে !
আর বিষাদময় কল্পনা আসে আর যায়
আমার স্বপ্ন জুড়ে, যখন একদিনের আর্তি
পূর্বাভাস দিয়ে যায় -- আমি জানি আগাম বিপদ !
ওহ, দুঃখ -- আর তুমিও দুঃখে ভুগছ, মিষ্টতায়,
নয়কি তুমি, এই দৃশ্য দেখে ? যদিও তোমার চোখ
সোনালী ও বেগুনি প্রজাপতিদের অনুসরণ করছে
যেগুলো আমাদের পায়ের কাছের জঞ্জালে ওড়াউড়ি করছে ।
নিঃশব্দে
গাঢ় গোধুলীর প্রশান্তি
গড়ে উঠেছে গাছগাছালির শাখায়
এসো স্তব্ধতা ও ছায়ার
এই প্রভাবকে শ্বাসে ভরে নিই ।
তোমার হৃদয়কে আমার হৃদয়ে মিশে যেতে দাও,
আর তোমার আত্মাকে পৌঁছোতে দাও আমার কাছে,
পাইনবনের স্নেহসিক্ত পরিবেশে
আর গুল্মের দীর্ঘশ্বাসের মাঝে ।
দুচোখ বোজো, তোমার দুই হাত রাখো
তোমার তন্দ্রাচ্ছন্ন হৃদয়ের ওপরে
যার নিয়ন্ত্রণ থেকে যাবতীয় অবিশ্বাস
চিরকালের জন্য চলে যায়, আর শিল্পীত হয়ে ওঠে ।
এসো সময় সঙ্গতিবিধান করুক !
এসো মৃদু বাতাসকে আসতে দিই,
রোদেপোড়া ঘাসেদের উড়িয়ে নিয়ে যাক,
আমাদের মনকে ধীরতায় নিয়ে আসুক !
আর যখন বাতাসের ভেতর দিয়ে রাত
ছুঁড়ে ফেলে দেবে তার জাঁকজমক-ভরা ছায়া
ছুঁয়ে যাবে আমাদের বিষণ্ণ কন্ঠস্বর,
বহুক্ষণ গান শোনাবে পাপিয়া
যেহেতু ছায়ারা আদ্রচিত্ত হয়
যেহেতু ছায়ারা আদ্রচিত্ত হয়, যেহেতি আজকেই সেই দিন,
যেহেতু আমি ভেবেছিলুম আশা চিরকালের মতো বিদায় নিয়েছে,
মেয়েটিকে ডাকে দিই প্রার্থনা করি ফিরে আসতে আমার কাছে,
যেহেতু অতো আনন্দ আমার নিজেরই অনুমোদন,--
সমস্ত কালো অভিসন্ধি আমি এখানেই পরিত্যাগ করছি,
আর যাবতীয় অশুভ স্বপ্ন । আহ, আমি ফুরিয়ে গেছি
সবার ওপরে কোঁচকানো ঠোঁটে, মুখ বেঁকিয়ে হাসা,
নির্দয় হাস্যকর উক্তি যখন দীর্ঘশ্বাস ফেলার কথা ।
যাও, মুঠিবাঁধা ঘুষি আর বুকের ক্রুদ্ধ ফুলে ওঠা,
যে বোকা আর মূর্খদের প্রতিটি মোড়ে দেখা যায় ।
যাও, কঠিন ক্ষমাহীনতা ! বিদায়,
ঘৃণিত চোলাইতে পাওয়া বিস্মরণ !
কেননা আমি বলতে চাই, এখন ভোরের এক প্রাণী
আমার রাত জুড়ে ছড়িয়েছে রশ্মির উদ্ভাস
যা প্রেমের যুগপৎ অমর ও সদ্যজাত,--
মেয়েটের হাসির কৃপায়, তার চাউনিতে, তার গরিমায়,
ওগো কমনীয় হাত, তুমি আমার হাত ধরে থাকো,
আমার হাত কাঁপে,-- তোমার মিষ্টি চোখের চাউনিতে,
সোজা হাঁটার জন্য, পথ তো শ্যাওলায় পিচ্ছিল
কিংবা পাথর আর পাথরকুচিতে ভরা উষর বিস্তার ।
হ্যাঁ, আমি জীবনের পথে শান্তিতে হাঁটতে চাই, এগোতে চাই,
ধৈর্য বজায় রেখে, গন্তব্যে পৌঁছোবার জন্য উদ্বেগহীন,
ঈর্ষা, হিংসা, কিংবা ঘৃণা থেকে মুক্ত
তা হবে উৎসাহী আত্মার কর্তব্য ।
আর যেমন আমি চাই, দীর্ঘপথকে আলোকিত করতে,
সাহসী আর নতুনবাঁধা গান গাইতে গাইতে,
মেয়েটি শুনবে আমার গান অমায়িকভাবে, আমি বলছি,--
আর, তাছাড়া, অন্য কোনো স্বর্গ আমি চাই না ।
তোমার আলো পুরোপুরি ব্যর্থ হবার আগে
তোমার আলো পুরোপুরি ব্যর্থ হবার আগে,
ইতিমধ্যে ক্ষয়িত হতে থাকা নক্ষত্র,
( তিতির পাখি
দূরের ঝোপে বসে গান গায় ! )
কবির চোখকে অন্যদিকে ফেরাও
প্রেম ছাপিয়ে চলে যায়---
( দেখতে পায় ভরতপাখি
দেখা করতে যাচ্ছে সূর্যের সঙ্গে ! )
তোমার চাউনি, যা এখন
ডুবে যাবে নীলাভ সকালে ;
( কী আনন্দ
খেতের পাকা ফসলের হাসিতে ! )
তাহলে আমার সত্যকার বার্তা পাঠিয়ে দাও
নিচের দিকে ওইখানে, -- অনেক দূরে !--
( শিশির
খড়ের ওপরে ঝিকমিক করছে ।)
দৃষ্টি যতোদূর দেখতে চায়
প্রিয়তমা যে ঘুমোচ্ছে এখনও ।
( তাড়াতাড়ি করো !
সূর্য পাহাড়ের কাছে পৌঁছে গিয়েছে ! )
বনানীর ভ্রুর ওপরে
বনানীর ভ্রুর ওপরে,
ফ্যাকাশে, তাকিয়ে আছে চাঁদ ;
প্রতিটি শাখায়
ভ্রাম্যমান হাওয়া
ফিকে দীর্ঘশ্বাস ফ্যালে…
হে হৃদয়ের আকাঙ্খা !
দুটি উইলো গাছ
দোল খায় আর কাঁদে,
একটি বাতাসে
অন্যটি গভীর বনে
স্রোতস্বিনী কাচ…
আমরা স্বপ্নের স্বপ্ন দেখি…
এক অসীম
হাতাশ্বাস
ঝরে পড়ে যেখানে শ্বেতাভ
কুয়াশা জ্যোতির্ময়
চাঁদের আলোক ঝর্ণায়…
থেকে যাও, নির্ভুল সময় !
গাড়ির জানালা দিয়ে দেখা দৃশ্য
গাড়ির জানালা দিয়ে দেখা দৃশ্য
প্রমত্ত উড়ালে পাশ দিয়ে দ্রুত চলে যায় ; সমগ্র প্রান্তর জুড়ে
জলধারা আর পাকা ফসলের খেত আর গাছ আর নীল
তাদের গিলে ফ্যালে ঘূর্ণাবর্ত, যার ভেতরে
টেলিগ্রাফের রোগাটে থামগুলো ঢলে পযেছে,
তাদের তারগুলো গানের স্বরলিপির মতন অদ্ভুত দেখায় ।
ধোঁয়া আর বাষ্পের এক গন্ধ, এক ভয়ঙ্কর হইচই
হাজার শেকলের ঝনঝনা যেমন বেঁধে রাখে
চাবকানো হাজার দানবের চিৎকারের মতন,--
আর হঠাৎই, এক পেঁচার দীর্ঘ চিক্কুর ।
আমার কাছে এগুলো কী ? কেননা আমার চোখে
যে দৃশ্য রয়ে গেছে তা পবিত্রতার,
এখনও মিহিন কন্ঠ আমার কানে অনুচ্চস্বরে বাজে,
আর যেহেতু তার নাম, এতো মধুর, এতো অভিজাত, এতো প্রিয়,
এই পাগল-করা ঘুর্ণির বিশুদ্ধ অক্ষ, কি ছেয়ে যায়
রেলপথের ওপরের নিষ্ঠুর ঝনঝনানিতে ?
আগুনের গোলাপি আঁচ, বাতির সঙ্কীর্ণ আভা
আগুনের গোলাপি আঁচ, বাতির সঙ্কীর্ণ আভা
ধ্যামগ্নতা বোধহয় এক স্বপ্ন
যে চাউনি নিজেকে হারিয়ে ফ্যালে অভীষ্ট সৌন্দর্যে ;
গরম চা আর বিসর্জিত বইয়ের সময় ;
সন্ধ্যার মাধুর্য ফুরিয়ে চলেছে,
প্রিয় কলআন্তি, আর বিশ্রামের অধিকার পাওয়া গেছে,
আর রাতের প্রত্যাশাকে অঞ্জলি দিয়েছি,--
ওহ, এই সমস্তকিছু, অকরূণ উড়ালে,
আমার স্বপ্ন অযথা কালহরণকে অনুসরণ করে,
সপ্তাহগুলো সম্পর্কে অধৈর্য, দিনগুলোতে উন্মাদ !
তাহলে, গ্রীষ্মের কোনো দিনে, ব্যাপারটা হবে
তাহলে, গ্রীষ্মের দিনে, ব্যাপারটা হবে :
সূর্য, আমার আনন্দসঙ্গী, ঝলমল করবে ঔজ্বল্যে,
আর তোমার রেশম ও সূক্ষ্ম সাটিনের খোলতাই করবে,
আরেক রশ্মি পর্যন্ত তোমার প্রিয় প্রতিভাস ;
স্বর্গেরা, এক দামি শামিয়ানার মতন
তাদের নীল ভাঁজগুলো ঝেড়ে ঝুঁকে লতিয়ে পড়বে
আমাদের হানন্দিত ভুরু ঘিরে, যা মিশে যাবে
প্রচুর আহ্লাদে, অনেক বেশি আকাঙ্খায় ;
আর যখন দিন শেষ হয়ে আসবে, বাতাস হয়ে উঠবে কোমল
খেলবে তোমার তুষারঢাকা ঘোমটায়, আদর করবে,
আর নরম হাসির চাউনি মেলে তাকিয়ে থাকবে নক্ষত্রের দল
বিবাহিত জুটির দিকে সানুগ্রহে ।
শহরে ধীরে ধীরে বৃষ্টি হচ্ছে -- আর্তুর র্যাঁবোকে
আমার হৃদয় ফোঁপায়
যখন শহরে বৃষ্টি পড়ে ।
কী এই নিস্তেজ জ্বালা
দখল করে রেখেছে আমার হৃদয় ?
বৃষ্টির নরম আওয়াজ
মাটিতে আর ছাদের ওপর !
ব্যথাকাতর এক হৃদয়ে
হে বৃষ্টির গান !
কারণ ছাড়াই তা ফোঁপায়
আমার অসুস্হ-হৃদয় হৃদয়ে ।
তার বিশ্বাসে, কী ? কোনো খাদ নেই ?
বিষাদের কোনো কারণ নেই ।
এটাই নিশ্চিত মন্দতম দুর্ভাগ্য
কে জানে কেনই বা
আমার হৃদয় যন্ত্রণায় ভোগে
কোনো আনন্দ বা আর্তি ছাড়াই ।
তার সুখী, অবাঞ্ছিত, বাজনার সুর - পেত্রুস বোরেলকে
পিয়ানোর রিড, যার ওপরে দুটি কোমল হাত ভাসছে,
গোধুলীর গোলাপি ও ধূসর রঙে অস্পষ্টতায় দীপ্ত,
যখন শব্দেরা ডানার মতন, ঝংকারের পর ঝংকার
উড়াল নিয়ে তৈরি করে বিষাদের ছোট্ট আদল
যা ঘুরে বেড়ায়, বিচক্ষণ ও কমনীয়, ক্ষীণ, বহু দূরের,
ঘরের ভেতরে যেখানে মেয়েটির সুগন্ধ পথ হারায় ।
কী এই আচমকা স্তব্ধতা আমাকে আদর করে
ওই সরল গানের স্বপ্নালু বিলম্বিত আর লঘু লয়ে ?
আমার কাছে তুমি কি চাও, ফ্যাকাশে সুর ?
তুমি কি চাইছ, ভুতুড়ে সঙ্গীত
যা ঢেউ খেলিয়ে জানালার দিকে মিলিয়ে যাচ্ছে
ছোট্ট বাগানে দরোজা খুলতে ?
ওহ, ভারি, বড়ো ভারি আমার বিষাদ,
কারণ, কারণ একজন কতো বেশি সুন্দরী ।
আমার দুর্দশা কোনো উপশম জানে না,
যদিও আমার হৃদয় ফিরে চলে এসেছে ।
যদিও আমার হৃদয়, যদিও আমার আত্মা,
প্রাণনাশকের নিয়ন্ত্রণ থেকে পালিয়ে এসেছে ।
আমার দুর্দশা কোনো উপশম জানে না,
যদিও আমার হৃদয় ফিরে চলে এসেছে ।
আমার হৃদয়, অনেক বেশি অনুভব করে,
আমার আত্মাকে বলে, “এটা কি করা যায়,
“এটা কি করা যায়, অনুভবকারী হৃদয়,
যে তাকে ছেড়ে আমরা আলাদা থাকব ?”
আমার আত্মা আমার হৃদয়কে বলে, “জানি আমি
এই অদ্ভুত পতনের মানে ঠিক কি ।
“আমরা, যদিও মেয়েটির থেকে দূরে, তবু কাছে,
হ্যাঁ, বর্তমান, তবুও এখানে নির্বাসিত ?”
“ একটি গাছের মগডাল থেকে পাপিয়া নিজের দিকে তাকায়
মনে করেন ও নদীতে পড়ে গেছে। অথচ ও মগডালে
একটি ওক গাছে, এবং তবুও সে ডুবে যাওয়ার ভয় পায়।”
সাইরানো দ্য বেরগেরাক
কুহেলী স্রোতধারায় গাছেদের প্রতিবিম্ব
প্রাণবন্ত স্রোতে মারা যায় ;
যখন সত্যিকারের ফুলের ঝোপে, একা,
কম বয়সী ঘুঘুপাখিরা শোকপালন করে ।
হে পর্যটক, কতো অস্পষ্ট মুখশ্রী, এই অস্পষ্টতা
ধূসর সমতলভূমির দিকে তাকিয়ে
আর গাছেদের মগডালে কতো একা
তোমার ডুবন্ত আশার বিলাপ !
ব্রাসেলস
দ্রুত চলে যায় পাহাড় আর ঝোপের বেড়া
সবুজ-গোলাপি উড়ালের সঙ্গে মিশে
আর ঘোড়ার গাড়ির হলুদ বাতি
আধবোজা চোখকে ঝাপসা করে তোলে ।
সোনালী রঙ ক্রমশ লাল হয়ে যায়
বিনয়ী অন্ধকার উপত্যকা জুড়ে ;
অবনত ছোটো ছড়ানো গাছেতে
দুর্বল পাখিশিশু একা বসে কাঁদে ।
বিরল দুঃখে, কতো নম্র আর স্পষ্ট
গুটিয়ে আসা এই হেমন্তঋতুকে মনে হয় ;
আমার সমস্ত খামখেয়ালি বিষণ্ণ স্বপ্নেরা,
মৃদু হাওয়ার কোলে দোল খায় ।
রাতের পাখিরা
১
প্রিয়তমা, তুমি আমার প্রতি ধৈর্য রাখতে পারোনি ;
ধৈর্যের এই অভাবকে যে-কেউ সঠিক বুঝতে পারবে :
তোমার বয়স অনেক কম ! যৌবন চিরকালই প্রখর
আর পরিবর্তনশীল ও হঠকারী !
তোমার ছিল না প্রয়োজনীয় দয়া, না ;
কারোর তাতে আশ্চর্য হবার কথা নয়, দুঃখবশত :
তোমার বয়স অনেক কম, শীতল বোন আমার, আর তাই
স্বাভাবিক যে তোমার কোনো সংবেদন নেই !
আমাকে জড়িয়ে ধরো ক্ষমা করে দিতে পারি তবে ;
আনন্দে নয়, অবশ্যই ! বরং যা সম্ভব তা-ই করতে চাই
সাহসে মুখোমুখি হবো,-- যদিও গভীর মন খারাপ হয়
হয়ে উঠব, তোমার মাধ্যমে, সবচেয়ে দুঃখী মানুষ ।
২
কিন্তু তুমি স্বীকার করবে যে আমিই সঠিক
যখন মনখারাপ অবস্হাব আমি বলতুম তোমায়
তোমার মধুর চাউনি, আমার আশা, একবার, আর পুলক !
দেখে মনে হতো এই দুটি চোখ বিশ্বাসঘাতকতা করবে ।
তা ছিল অশুভ মিথ্যা, তুমি দোহাই দিয়ে বলতে,
আর তোমার দৃষ্টি, যা মিথ্যাকথা বলত, প্রিয়তমা, আগুন ধরাতো,--
বেচারা আগুন, প্রায় নিভন্ত, তাকে ঘাঁটিয়ে কেউ লেলিহান করতে চায় !’’
আর তোমার কোমল কন্ঠে তুমি বলতে, “আমি তোমাকে ভালোবাসি !”
হায় ! কারোর উচিত আনন্দকে আঁকড়ে ধরা
ইন্দ্রিয় দিয়ে, ঋতু দিয়ে, যাই হবে যাক না কেন !--
কিন্তু তা ছিল এক ঘণ্টার উল্লসিত তিক্ততা
যখন আমি নিশ্চিত হলুম যে আমিই ছিলুম সঠিক !
৩
আর কোথায় আমি মেলে ধরব আমার হৃদয়ের আঘাত ?
তুমি আমাকে ভালোবাসো না, -- সেখানেই শেষ, আমার নারী ;
আর যেহেতু আমি সাহস করে বেছে নিইনি
কৃপার ভিক্ষা, -- আমাকে কষ্টভোগ করতে হবে মুখবুজে ।
হ্যাঁ, কষ্টভোগ ! কারণ আমি তোমায় গভীর ভালোবেসেছি, বাসিনি কি,--
কিন্তু অনুগত সৈনিকের মতন আমি দাঁড়িয়ে থাকব
আঘাতে মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত, টলতে টলতে মারা যাওয়া,
তবু অকৃতজ্ঞের জন্যও ভালোবাসায় পরিপূর্ণ ।
ওগো তুমি ছিলে আমার সুন্দরী আর আমার নিজস্ব,
যদিও তোমার কারণে আমাকে বহু দুর্ভোগ পোয়াতে হয়েছে,
তবু তুমি আর গৃহের হতে পারোনি, তাহলে, তুমি একা,
ফ্রান্সের মতন কম বয়সী আর উন্মাদ আর সুন্দরী ?
৪
এখন আমি আর চাই না -- কীই বা পাবার আছে ?--
অতীতের ভাবনায় অশ্রুজলে বসবাস করে ;
তবু হে নারী তুমি হয়তো ভাবো প্রেম পড়ে আছে কোতল হয়ে,
হয়তো শেষ পর্যন্ত দুই চোখ মেলে জেগে রয়েছে ।
হে নারী, হয়তো, -- যা এখন স্মৃতি ! --
যদিও তোমার ভ্রুর তলায় চোখের পাতা নামানো ও কান্না
আর রক্তাক্ত ইচ্ছা, আর নিশ্চয়ই, আমি দেখতে পাচ্ছি আগাম,
দীর্ঘকাল কষ্ট ভোগ করবে আমি মারা যাবার আগে, -
তোমাকে যথার্থ বিচার করে যখন বুঝতে পারে
সবকিছুই তুচ্ছ সংযোগ নয়,
আর বিষাদে আক্রান্ত তোমার স্মৃতি
তোমাকে কলঙ্কিত করে, “আহ, অশুভ উপায়ে কেন !”
৫
এখনও দেখতে পাই তোমায় । আলতো খুলেছিলুম দরোজা--
ক্লান্তিতে অবসন্ন তুমি শুয়েছিলে ;
কিন্তু অপলকা দেহকে জাগিয়ে তুলবে প্রেম,
তুমি বাঁধনে জযিয়েছ, একই সঙ্গে কান্না আর আহ্লাদে ।
কতো জড়াজড়ি, মিষ্টি বেপরোয়া চুমু !
আমি, উজ্বল চোখে হেসেছি তোমায় দেখে
সেই সব মুহূর্ত, অনেকের মাঝে, হে কমনীয় খুকি,
আমার সবচেয়ে দুঃখের, কিন্তু মধুরতমা,
তোমার হাসি আমি মনে রাখব, তোমার আদর,
তোমার দুই চোখ, কতো সদয় ছিল সেদিন, -- নিখুঁত ফাঁদ !--
তোমার ছাড়া আর কারই বা মহিমা গাইব না,
যেমনটা দেখলুম, যেমন দেখেছিলুম নয় ।
৬
আমি আজও দেখতে পাই তোমায় ! গ্রীষ্মের পোশাকে,
হলুদ আর শাদা, পরদার ফুলে ছয়লাপ ;
কিন্তু তোমার হাসির দীপ্তি হারিয়ে ফেলেছিলে তুমি
আমাদের পুরোনো দিনের মনমাতানো প্রেমের ।
বড়ো মেয়ে আর ছোট্ট বউ
যৎসামান্য বলেছিল তোমার বিষয়ে,--
আগেই তো হায় ! আমাদের বদলে যাওয়া জীবন
আমার দিকে তাকিয়েছিল তোমার আবরুর জাল থেকে ।
আমাকে ক্ষমা ! আর একটুও গর্বে নয়
আমি তৈরি ছিলুম,-- আর তুমি, সন্দেহ নেই, দেখেছো তো কেন,--
একদিকে বিদ্যুত-আলোর স্মৃতি
যা তোমার রাগি চোখ থেকে ঝলকাতো !
৭
অনেক সময়ে, আমি ঝড়ে ওপড়ানো ছাল
যা মাস্তুল থেকে খসে জলোচ্ছাসে দৌড়োয়,
আর অন্ধকারে ভার্জিন মেরিকে দেখতে না পেয়ে
ডুবে যাবার জন্য তৈরি হয়, আর প্রার্থনায় হাঁটু গেড়ে বসে ।
অনেক সময়ে, আমি তার প্রান্তের পাপী,
যে তার সর্বনাশের কথা জানে যদি সে অবিশ্বাস নিয়ে যায়,
আর কোনো ভুতুড়ে বন্ধুর আশা ত্যাগ করে
নরকের খোলা দরোজা দেখতে পায়, অনুভব করে তার উদ্ভাস ।
ওহ, কিন্তু ! অনেক সময়ে, আমার উদ্দীপনা দুর্দম
সিংহের আশ্রয়ে প্রথম খ্রিষ্টধর্মির মতন,
যিশু যে হাসির সাক্ষী ছিলেন, স্নায়ুর
কোনো বেয়াড়াপনা ছাড়াই, একটা চুলও নাড়াতে পারেনি !
সবুজ
দ্যাখো, ফুলের তোড়া, গাছের শাখা, ফল, পাতা নিয়ে এসেছি,
আর আমার হৃদয় যা তোমার জন্যই শ্বাস নেয় ;
তোমার ওই শ্বেতাভ হাতে, ওহ, ছিঁড়ে ফেলো না,
কিন্তু গরিবের উপহার তোমার দৃষ্টিতে শ্রীবৃদ্ধি করুক ।
আমার মাথার শিশির এখনও শুকোয়নি,--
সকালের বাতাস যেখানে আঘাত করে শীতলতা আনে ।
তোমার কাছে এসে ক্লান্তির যন্ত্রণা ভোগ করি
সেই সময়ের স্বপ্ন দেখার জন্য যা নিষ্পত্তি করে দেবে ।
আমার মাথাকে তোমার বুকে রাখতে দাও
যা তোমার অন্তিম চুমুগুলোয় প্রতিধ্বনিত হয়
বিষাদ
গোলাপগুলো কতো লাল ছিল, কতো লাল
আইভিগুলো একেবারে কালো ।
তুমি একবার এই দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলে,
প্রিয়তমা, আমার সমস্ত বিষাদ ফরে এলো !
আকাশ ছিল মিষ্টিমধুর আর নীল,
সাগর দেখাচ্ছিল দ্রবীভূত সবুজ ।
আমার সব সময়ে ভয় করে, -- যদি তুমি তা জানতে !--
তোমার প্রিয় হাত দিয়ে এক হত্যার আঘাত ।
শূলপর্ণী গাছের ক্লান্তি আমার
আর ঝলমলে বাক্সের ও ঢেউখেলানো ঘাসের
অশেষ বিস্তীর্ণ চারণভূমির ওপরে,--
আর তুমি শুধু তুমি ছাড়া কেউ নয়, হায় !
পথগুলো
এসো দ্রুততালে নাচি !
সবার ওপরে আমি ওর চোখদুটো ভালোবাসতুম,
মেঘহিন আকাশের নক্ষত্রদের চেয়েও স্পষ্ট,
আর পুলকিত আর দুষ্টু আর বুদ্ধিমতী ।
এসো দ্রুততালে নাচি !
এতো দক্ষতায় এগোবে মেয়েটি
রক্তাক্ত করবে প্রেমিকের উন্মুক্ত হৃদয়,
তা ছিল সত্যিই সুন্দর !
এসো দ্রুততালে নাচি !
কিন্তু গভীরভাবে উপভোগ করেছি
ওর লালঠোঁটের চুমু
কারণ আমার হৃদয়ে ও তো মারা গেছে ।
এসো দ্রুততালে নাচি !
অবস্হাবিপাকে বড়ো আর ছোটো,--
শব্দেরা, মুহূর্তেরা...মনে পড়ছে আমার, মনে পড়ছে
সবকিছুর মাঝে এটাই আমার ঐশ্বর্য ।
এসো দ্রুততালে নাচি !
মিথ্যা চমৎকার দিনগুলো
মিথ্যা চমৎকার দিনগুলো আগুন ধরিয়েছে জীবনের সময়ে,
তবু তারা রুক্ষ পশ্চিমে ফুলকি জ্বালে ।
চোখ নিচে নামাও, বেচারা আত্মা, যে আশীর্বাদ পায়নি তাকে রুদ্ধ করো :
কুকর্মের এক মারাত্মক ফাঁদ । চলে এসো ।
সারাটা দিন ওরা আগুনের আলো দেখিয়েছে, পড়ে আছে
পাহাড়ের সবুজ বুকের ওপরে নীচ মদিরা ।
ফসল বেশি হয়নি, -- আর যারা সবচেয়ে বিশ্বাসী,
নীল আকাশ তাকিয়ে আছে সব সময়, হতাশা ত্যাগ করো ।
ওহ, হাত জোড় করো, ফ্যাকাশে হও, আবার ফিরে চাও !
যদি অতীত দিয়ে সমস্ত ভবিষ্যৎ উপলব্ধ হয় ?
যদি পুরোনো উন্মাদনা ফিরে আসে ?
সেইসব স্মৃতি, প্রতিটিকে কি আবার কোতল করতে হবে ?
এক জবরদস্ত আক্রমণ, সবচেয়ে ভালো, নিঃসন্দেহে, শেষতম !
যাও আসন্ন ঝড়ের বিরুদ্ধে প্রার্থনা করো, যাও প্রার্থনা করো !
নীলাকাশ ছাদের ওপরে হাসে
নীলাকাশ ছাদের ওপরে হাসে
তার কোমলতম ;
আক সবুজ গাছ ছাদের ওপরে উঠে যায়
মাথা দোলায় ।
বাতাসহীন আকাশে গির্জার ঘণ্টাধ্বনি
শান্তিতে বাজে,
আকাশে বহুদূরে উড়ে এক শাদা পাখি
অবিরাম গান গায় ।
হে ঈশ্বর, আমার ঈশ্বর, সমস্ত জীবন পড়ে আছে,
সরল ও মধুর ;
মৌচাকের আরামপ্রদ গুঞ্জন
রাস্তা থেকে ভেসে আসে !
কী তুমি করেছ, ওহে তুমি তো কাঁদছ
আনন্দের সূর্যালোকে, --
বলো, তোমার যৌবন নিয়ে, তুমি যে কাঁদছ,
কী করেছ তুমি ?
অবসন্নতা
ফুরিয়ে আসার শেষ পর্যায়ে আমি এক সাম্রাজ্য,
যা দেখতে পায় ঢ্যাঙা, পরিস্কার চুলের বর্বররা চলে যাচ্ছে, -- ততক্ষণ
অবান্তর ছন্দোবদ্ধ গাথা রচনা করে, সে এক শৈলীতে
সোনালী, তার প্রতিটি ছত্রে নাচছে নির্জীব রোদ ।
নিঃসঙ্গ আত্মা এক দুশ্চরিত্রতায় হৃদরোগাক্রান্ত
অবসাদে । তুমি পতিত, ওরা বলে, যুদ্ধের মশাল রক্তকে উজ্বল করে ।
হায়, দুর্বল ইচ্ছাশক্তির কারণে, ফিরে আসা দরকার
সাহসী অ্যাডভেঞ্চারের সুযোগ থেকে--
মৃত্যুর, যদি আচমকা ঘটে ! হায়, আকাঙ্খাহীন !
আহ, সবাই তো মাতাল ! ব্যাথিলাস ওর হাসি হেসে নিয়েছে, নাকি ?
আহ, সবাই তো মাতাল, -খাওয়া হয়ে গেছে ! বলবার আর কিছু নেই !
একা, একজন আগুনে ফেলে দ্যায় নীরস কবিতা ;
একা, একজন চোর ক্রীতদাস আরেকজনকে অবহেলা করছে ;
একা, এক অস্পষ্ট বিরক্তি সূর্যের তলায় !
ভুয়া মুদ্রণ
বুড়ি ইঁদুর বকবক করে
ধূসর ছায়ায় কালো ;
বুড়ি ইঁদুর বকবক করে
কালোর আড়ালে ধূসর ।
ঘুমোবার কাঁসরঘণ্টা শোনো !
তক্ষুনি ঘুমোও, ভালো কয়েদিরা ;
ঘুমোবার কাঁসরঘণ্টা শোনো !
তোমাকে যেতেই হবে ঘুমোতে ।
স্বপ্নে ব্যাঘাত চলবে না !
তোমার ভালোবাসা ছাড়া আর কিছু ভেবো না :
স্বপ্নে ব্যাঘাত চলবে না,
সুন্দরীদের কথা ভাবো !
চাঁদের আলো স্পষ্ট আর ঝকমকে !
পাশে কেউ একজন নাক ডাকছে ;
চাঁদের আলো স্পষ্ট আর ঝকমকে--
ওই লোকটা ঝামেলা বাধায় ।
এসে পড়েছে এক ভুষোমাখা মেঘ
ফ্যাকাশে চাঁদের ওপরে হামাগুড়ি দিয়ে ;
এসে পড়েছে এক ভুষোমাখা মেঘ--
দেখার জন্য ধূসর সকাল আসছে গুঁড়ি মেরে !
বুড়ি ইঁদুর বকবক করে
নীলাভ রশ্মি জুড়ে গোলাপি ;
বুড়ি ইঁদুর বকবক করে…
অপদার্থরা, উঠে পড়ো ! সকাল হয়েছে !
ভবিষ্যতে আর নয়
স্মৃতি, তুমি আমার সঙ্গে কী করতে চাও ? বছর
ফুরিয়ে এলো ; স্হির বাতাসে পাখির স্পষ্ট গান,
অলস রোদ অনুৎসাহী উঁকি মারছে না
বনানীর শুকনো ঝরা পাতাদের মাঝে ।
আমরা ছিলুম একা, আর চিন্তামগ্ন ঘুরে বেড়ালুম,
কল্পনায় ইতিউতি জড়াজড়ি করছিলুম, যখন, আরে
মেয়েটি তার রোমাঞ্চকর চাউনিকে মেলে ধরল,
আর ওর তরল সোনার কন্ঠে আমাকে জিগ্যেস করল,
ওর টাটকা তরুণী গলায়, “কবে ছিল সবচেয়ে আনন্দের দিন ?”
আমি বিচক্ষণ হাসিতে উত্তর দিতে চাইলুম, আর
নিষ্ঠার সাথে ওর ফর্সা হাতে চুমু খেলুম !
--আহ, আমি ! প্রথম ফুলগুলো, ওরা কতো মধুর !
আর কি উৎকৃষ্ট এক ফিসফিস ফাঁস করে
প্রথমতম “হ্যাঁ” ভালোবেসে পাওয়া ঠোঁট থেকে !
তিন বছর পরে
বাগানের সরু দরোজাটা যখন ঠেললুম,
আরেকবার দাঁড়ালুম সবুজ অপসরণের মাঝে ;
সকালের নরম রোদ তাকে আলোকিত করে দিলো,
আর প্রতিটি ফুল পরে নিলো তাদের আদ্র জামার চুমকি ।
কিছুই বদলায় না । আমি আরেকবার তাকিয়ে দেখি :
আঙরলতার কুঞ্জবন তার দেহাতি আসনে বসে..
ফোয়ারা এখনও মধুর রুপো ছেটায়,
প্রাচীন ধ্বনিরা এখনও আগের মতো মর্মরিত হয় ।
গোলাপেরা স্পন্দিত হয় বিগত দিনের মতোই,
যেমন তাদের অভ্যাস ছিল, গর্বিত লিলিফুল দোল খায়
প্রতিটি পাখির উড়ে যাবার সময়ের ডাক এক বন্ধুর ।
আমি এমনকি ফ্লোরাকে এখনও দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলুম,
যার পলেস্তারা গলিপথের শেষে খসে পড়ছে
--একহারা, মিগনোনেট ফুলের বোকা গন্ধের মাঝে ।
আমার পারিবারিক স্বপ্ন
প্রায়ই আমি গভীর অন্তর্দৃষ্টির এই অদ্ভুত স্বপ্ন দেখি :
এক অচেনা নারী, যাকে ভালোবাসি, যে আমাকে খুবই ভালোবাসে,
যে কখনও বদলায় না, কিন্তু ভালোও থাকে না
সেই একই, -- আর আমাকে খুব ভালোবাসে, আর জানে আমি কেমন লোক ।
কেননা ও আমাকে জানে ! আমার হৃদয় স্ফটিক রশ্মির মতো স্পষ্ট
কেবল সে, তার অনির্বচনীয়তাকে ক্ষান্তি দ্যায়
কেবল সে, আর শুধু সেই জানে কেমন করে নিরসন করতে হবে
আমার দুঃখ, তার অশ্রুফোঁটা দিয়ে শীতল করে আমার ভ্রু ।
সে কি শ্যামলী কিংবা ফর্সা ? আমি জানি না ।
তার নাম ? আমি যেটুকু জানি প্রবাহিত হয়
কোমলতায়, সেই লোকেদের মতো যারা ভালোবেসে হেরে গেছে ।
তার চোখদুটি প্রতিমার মতো, -- মৃদু আর গভীর আর অপলক ;
আর তার কন্ঠস্বর যেন তা সেইসব প্রেতের
কন্ঠস্বর, -- যে কন্ঠস্বরেরা ভালোবাসা পেয়ে মারা গেছে ।
একজন নারীকে
এই পংক্তিগুলো তোমাকে করুণার সান্ত্বনার জন্য
তোমার দীঘল চোখের জন্য যেখানে কোমল স্বপ্নেরা দীপ্ত হয়,
তোমার বিশুদ্ধ আত্মার জন্য, খুবই দয়ালু ! -- এই পংক্তিগুলো তোমাকে
আমার অপ্রতিম মর্মপীড়ার কৃষ্ণগহ্বর থেকে ।
এই ঘৃণ্য স্বপ্ন যা নিপীড়ন করে
আমার আত্মাকে, হায় ! এর দুঃখি শিকার কখনও হাল ছাড়ে না,
কিন্তু এক পাল নেকড়ের উন্মত্ত তাড়ার মতন
আমার রক্তাভ পদচিহ্ণকে অনুসরণ করে তপ্ত হয়ে ওঠে !
আমি যন্ত্রণায় ভুগি, ওহ, আমি নিষ্ঠুরতা সহ্য করি !
যাতে স্বর্গোদ্যানের আদি পুরুষের কান্না হারিয়ে যায়
তা ছিল আমার কান্নায় গড়া মেঢো কবিতা !
আর যে দুঃখগুলো, প্রিয়তমা, ঘটেছে
তোমার জীবনে, তা কেবল উড়ন্ত পাখি
--পপিবতমা ! -- সেপ্টেম্বরের উষ্ণ সোনালী আকাশে ।
হেমন্তের গান
পাতা ওড়ানো ঝড়ে
মিহিস্বর রোদন
বেহালার মতন,--
আমার আত্মায়
তাদের লতানো দুঃখ
লুকিয়ে জিতে যায়….
দীর্ঘকাল কেটে গেছে !
তেমন সময়ে, আমি,
শ্বাসরুদ্ধ আর ফ্যাকাশে
তোমার কথা ভাবি,--
তারপর বাতাসের মতো
ফোঁপাই আর কাঁদি ।
আর, বাতাসের মতো
রুক্ষ ও নির্দয়
দুঃখে তাড়িত
আমি যাই, এখানে, সেখানে,
বুঝি না কোথায় যাচ্ছি
ঝরা পাতার মতন ।
 পল ভেরলেন | 122.179.172.247 | ২৪ আগস্ট ২০২১ ১৯:২৭734900
পল ভেরলেন | 122.179.172.247 | ২৪ আগস্ট ২০২১ ১৯:২৭734900পল ভেরলেন-এর পঁচিশটি কবিতা
গদ্যানুবাদ : মলয় রায়চৌধুরী
পদত্যাগ
যখন ছোটো ছিলুম, কোহিনুরের স্বপ্ন দেখতুম,
পারস্য আর পোপের ধনসম্পতি, মহার্ঘ,
সম্রাট হেলিওগাবালুস, রাজা সারদানাপালুস !
আমার ভাবনা ভরে যেতো, যেখানে সোনার ছাদ উঠে যায়,
সঙ্গীতের মূর্চ্ছনায়, যেখানে সুগন্ধ ফাঁদ পেতে ধরে,
অসংখ্য হারেম, দেহের স্বর্গোদ্যান !
এখন মন শান্ত তবুও কম আকুল নয়,
জীবনকে জানার পর, একজনকে কেমন বাধ্য হতে হয়,
অমন মনোরম বোকামিকে সামলাতে বলা হয়েছে আমায়,
আর তবুও খুব বেশি ছাড় দেওয়া যাবে না ।
তবে তাই হোক, সদিচ্ছাকে যদি মহানতা এড়িয়ে যায়,
তবু সাধারণ আর শিষ্টের স্তরে গিয়ে নামতে হবে !
কেবল সুন্দরী বলে আমি চিরকাল সে-নারীকে ঘৃণা করেছি
ছন্দ যা স্বরসাদৃশ্যে ভরা, বন্ধু যে বিচক্ষণ !
কখনও বেশি নয়
স্মৃতি, স্মৃতি আমার কাছে কি তুমি চাও ? হেমন্ত
রঙহীন বাতাসের ভেতর দিয়ে গায়ক পাখিকে উড়াল দ্যায়,
আর সূর্য তার একেঘেয়ে রশ্মি ছড়ায়
হলুদ-হয়ে-আসা বনানীতে যেখানে গান গায় উত্তরের হাওয়া ।
আমরা ছিলুম একা, আর চলাফেরা করছিলুম স্বপ্নে,
মেয়েটি আর আমি, বাতাসে বিপর্যস্ত চুল আর চিন্তা ।
তারপর, নিজের দুশ্চিন্তিত চাউনি আমার দিকে মেলে,
‘তোমার সবচেয়ে ভালো দিন ?’ ওর সোনালি কন্ঠস্বরে,
ওর কথা, দেবদূতের সুরে, তরতাজা, স্পন্দিত, মিষ্টি ।
আমি উত্তর দিলুম ওকে, বেশ বিবেচক মৃদু হাসি,
আর ওর শাদা হাতে অর্চকের চুমু রাখলুম ।
-- আহ ! প্রথম ফুলগুলো, কতো তাদের সুবাস !
আর কতো কমনীয় আবেগের গুঞ্জন
যে ঠোঁট ভালোবাসি তার প্রথম পাওয়া ‘হ্যাঁ !
তিন বছর পর
সরু নড়বড়ে গেট খুলে,
আমি পায়চারির জন্য গেলুম ছোট্ট বাগানে,
উজ্বল হয়ে উঠেছে সকালের সহৃদয় রোদে,
জলীয় আলোয় নক্ষত্র করে তুলেছে প্রতিটি ফুলকে ।
বদলায়নি কিছুই । আবার : নম্র কুঞ্জবন
বুনো লতাপাতায় আর দড়ি দিয়ে তৈরি চেয়ার…
ফোয়ারা সেই একইরকম রুপালি নকশায়,
আর শাশ্বত কাঁপুনিভরা বুড়ো পপলার গাছ ।
তখনকার মতো এখনও গোলাপেরা দুলছিল, আর তখনকার মতো
বাতাসে ঢুলছিল দীর্ঘাঙ্গী লিলিফুলের দল ।
সেখানের ভরতপাখিদের আমি চিনতুম, যাওয়া আসা বজায় রেখেছে ।
খুঁজে পেলুম জার্মান মহিলা সন্ত ভাদেলার মূর্তি তখনও দাঁড়িয়ে,
পথের শেষে পলেস্তারা খসে পড়ছে,
সময়ের ক্ষয়ে, সবুজাভ ফুলের স্নিগ্ধ সুবাসের মাঝে ।
ইচ্ছা
আহ ! অনুরাগী কথা ! আর প্রথম রক্ষিতারা !
চুলের সোনা, চোখের নীল, মাংসের কুসুম,
তারপর, প্রিয় দেহের ফাঁদের সুগন্ধে
আদরের লাজুক ফুর্তি !
এখন সেইসব লঘিমা থেকে কতো দূরে
আর সেইসব সরলতা ! আহ, তবুও পেছন পানে,
কালো শীত থেকে চলে গেছে, পরিতাপের বসন্তঋতুতে,
আমার বিষাদ, আমার ক্লান্তি, আমার দুর্দশা থেকে ।
তাই আমি এখন একা, এইখানে, দুঃখি ও নিঃসঙ্গ,
দুঃখি আর হতাশ, বুড়োদের মতো ভয়ে চমকিত,
যেন বড়ো দিদি নেই এমনই দরিদ্র অনাথ ।
ভালোবাসে এমন নারীর জন্য, কোমল ও ধীর,
মিষ্টি, ভাবুক, শ্যামলী, আর সারাক্ষণ অবাক,
যে তোমার ভ্রূযুগলে একজন খুকির মতো যখন-তখন চুমু খায় ।
অবসাদ
( ‘For the wars of love a field of feathers’, Gangora )
মাধুরী মিশিয়ে, মাধুরী মিশিয়ে, মাধুরী মিশিয়ে !
আমার সন্মোহিনী, একটু শান্ত করো এই জ্বরের বিদার ।
একজন প্রেমী, অনেক সময়ে, তুমি জানো, এমনকি তার মহিমায়
একটি দিদির চুপচাপ বিস্মৃতির অভ্যাস চায় ।
ধীরুজ হও : তোমার আদরগুলো এনে দিক ঘুম,
তোমার দোলনা-দোলানো চাউনি আর দীর্ঘশ্বাসের মতন ।
আহ, জড়িয়ে ধরার ঈর্ষা, বড়োবেশি অঙ্গগ্রহ,
এক গভীর চুমুর মতো নয়, এমনকি মিথ্যা চুমুরও !
কিন্তু তুমি আমাকে বলো, খুকি : সোনায় গড়া তোমার হৃদয়ে
আরণ্যক ইচ্ছারা ক্রন্দন ছড়ায় ।
মেয়েটিকে হইচই করতে দাও, ও বড়োই সাহসী !
তোমার ভ্রূযুগল আমার ভ্রুযুগলে রাখো, তোমার হাত আমার হাতে,
প্রতিজ্ঞা করো সেইসব যা তুমি একে -একে ভেঙে ফেলতে চাও,
ভোর অব্দি কাঁদবো দুজনে, আমার ছোট্ট জ্বলাময়ী !
আমার অন্তরঙ্গ স্বপ্ন
প্রায়ই এই স্বপ্ন দেখি আমি, অদ্ভুত, অন্তর্দৃষ্টিতে গভীর,
সে এক নারীর, অজানা-অচেনা, যাকে ভালোবাসি, সেও আমায়,
আর যে প্রতিবার থাকেনাকো একইরকম,
একেবারে আলাদাও নয় : অথচ আমাকে চেনে, ভালোবাসে ।
ওহ কেমন করে চেনে সে আমাকে, আমার হৃদয়, জেগে ওঠে
স্পষ্ট তারই জন্য শুধু, তা তো কোনো সমস্যা নয়,
কেবল তারই জন্য : সেই শুধু বোঝে, তারপর
কেমন করে যে তার কান্না দিয়ে আমার ভুরুর ঘাম পুঁছি ।
সে কি শ্যামলী, শ্বেতাঙ্গিনী, নাকি পিঙ্গল ? -- জানিনাকো আমি ।
তার নাম ? মনে আছে তা অতি স্পন্দমান আর প্রিয়,
যেন বা তাদের মতো জীবন নির্বাসিত করেছে যাদের ।
চোখ তার সেরকমই যেমন কোনো প্রতিমার চোখ,
আর তার কন্ঠস্বর, দূরাগত, সুগম্ভীর, মৃদু,
তার কন্ঠের স্বরাভাষ, যারা মারা গেছে ঠিক তাদের মতন ।
প্যারিসের দৃশ্য
চাঁদ তার দস্তার আবরণ খুলে ফেলছিল
অবিচ্ছিন্ন কোণাকুনিভাবে ।
ধোঁয়ার পালকগুলো পঞ্চমের মতো খুবই আলাদা
জোড়বাঁধা উঁচু ছাদ থেকে ঘন আর কালো উঠে যায় ।
আকাশ ধূসর ছিল, কাঁদছিল সে এক মৃদু হাওয়া
বাঁশের বাঁশির মতো ।
অনেকটা দূরে, হুলো-বিড়াল এক, চোরের মতন, চুপচাপ,
ডাক দেয়, ওহ, অদ্ভুত বেসুরো ।
আমি, হাঁটছিলুম, দিব্য প্ল্যাটোর স্বপ্ন
আর ফিদিয়ার,
সালামির, ম্যারাথন, ঝিলমিল-বোলানো নজরে
অজস্র চোখ, বাষ্পের নীলাভ চোখের উৎসারে ।
এক রহস্যময় সন্ধ্যার গোধুলী
গোধুলীর দীপ্তিময় স্মৃতি
আর আগ্নেয় দিগন্তের কম্পন
জ্বলন্ত আশার যা গুটোয় আর বেড়ে যায়
কোনো রহশ্যময় পরদার মতো
যেখানে অমিতব্যয়ী ফুলেদের দল
-- ডালিয়া, লিলি, টিউলিপ আর গ্যাঁদাফুল --
জাফরির চারিধারে ঘুরপাক খায়
মাতাল হাওয়ায়
পৃথু সৌরভের, যার উষ্ণতার বিষ
-- ডালিয়া, লিলি, টিউলিপ আর গ্যাঁদাফুল --
আমার ইন্দ্রিয়, আত্মা আর যুক্তিবোধ বিহ্বল করে,
তাদের প্রগাঢ় বিভ্রমে টেনে নেয়
গোধুলীর দীপ্তিময় স্মৃতি ।
সন্ধ্যা
কুয়াশাছায়া দিগন্তে রক্তবর্ণ চাঁদ ;
নৃত্যরত কুহেলিকায়, গোচারণভূমি
ধোঁয়ায় ঘুমোয়, নীচে ব্যাঙেদের দল
সবুজ নলবনে যেখানে শীতলতা বয় ;
দরোজা বন্ধ করে নেয় লিলিফুল,
পপলার গাছেরা ছড়িয়েছে বহুদূর,
দীর্ঘ আর পাশাপাশি, তাদের অপচ্ছায়ারা খাপছাড়া ;
জোনাকিরা ঝোপের ভেতরে শিখা জ্বালে ;
পেঁচারা জেগে আছে, শব্দহীন তাদের উড়ালে
ভারি ডানা দিয়ে বাতাসে তারা দাঁড় বায়,
ভরে ওঠে সুবিন্দু, বিষণ্ণতায় দ্যুতিমান ।
পাণ্ডুর শুকতারা দেখা দ্যায়, আর রাত্রি নেমে আসে ।
পাপিয়া
পাখিদের উচ্চরব উড়ালের মতো, জটিল অন্ধকার,
আমার সমস্ত স্মৃতি আমাকে বিধ্বস্ত করে চলে,
হলুদ পাতাদের মাঝে দিয়ে নামে প্রহরণ
আমার হৃদয়ের অবনত ভূর্যগুঁড়িতে, তার দৃষ্টিপাত
অনুতাপের জলরাশিতে ছায় রুপালি অরূণ
যার বিষাদময়তা এখনও স্রোতোস্বিনী,
নামে প্রহরণ, আর তারপর অশুভ অনুচ্চস্বর
যাকে এক উড়ন্ত আদ্র বাতাস সেখানে থামায়,
পাতাদের মাঝে ক্রমে মারা যায়, তাই
মুহূর্তের মধ্যে তুমি শুনতে পাবে না কিছুই, ওহ,
অনুপস্হিতকে প্রশংসা করার স্বর থেকে বেশি কিছু নয়,
কন্ঠস্বরের থেকে বেশি কিছু নয় - ওহ, কাতরতা ! --
পাখিটির, আমার প্রথম প্রেম, যা এখনও গান গায়
যেমন গাইতো গান বহুকাল আগেকার প্রথম সন্ধ্যায় ;
আর চাঁদের বিষাদময়ী ঐশ্বর্যের নীচে
ম্লান একাকীত্বে জেগে ওঠে, জুনমাসের এক
রাত, অবসাদময়, গ্রীষ্মের চাপে দুর্বহ,
নৈঃশব্দ ও অন্ধকারে পরিপূর্ণ, নীলচে আলোয়
মৃদু বাতাস যাকে আলতো ছোঁয়, দোলায় তন্দ্রায়
সেই গাছটিকে যা কেঁপে-কেঁপে ওঠে, যে পাপিয়া ফুঁপিয়ে গান গায় ।
নারী ও বিড়াল
ওর বিড়ালকে নিয়ে খেলছিল মেয়েটি :
ভালো লাগছিল তাকে দেখে
শাদা হাত আর শাদা থাবা
সন্ধ্যার ছায়ায় খেলা করে ।
মেয়েটি লুকায় -- ছোট্ট দুষ্টুর মতো !--
রেশমের কালো দস্তানাতে
খুনি মণিরত্ন-নখর,
বিড়াল-শিশুর মতো কোপন ও উজ্বল ।
অন্যজনও ছিল মধু-ওপচানো
আদরের তীক্ষ্ণনখ দস্তানা থেকে বের করে,
যদিও শয়তানটা এ-ব্যাপারে মন্দ ছিল না…
আর শোবার ঘরটিতে, সুরেলা যেখানে
স্বর্গীয় হাসি বাতাসে তুলছিল ঝংকার,
সেখানে ফসফরাসের চারটি বিন্দু ছিল দীপ্তিময় ।
শিল্পহীনদের গান
আমরা আসলে সবাই শিল্পহীন,
চুলেতে বিনুনি, দুই চোখ নীল,
গোচরতা থেকে যেন বা লুকিয়ে
উপন্যাসে পাওয়া যাবে না তাদের ।
আমরা হাঁটি, বাহুতে গলিয়ে বাহু,
আর দিনটি বিশুদ্ধ নয় আজ
যেমন আমাদের চিন্তার গভীরতা,
আর আমাদের নীলাভ স্বপ্ন ।
আর আমরা খেতের ভেতর দিয়ে দৌড়োই
আর আমরা হাসি আর আমরা গুলতানি করি,
সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত,
আমরা প্রজাপতিদের ছায়ার পেছনে দৌড়োই :
আর মেষপালিকাদের শিরাবরণ
আমাদের তরতাজা রাখে
আর আমাদের পোশাক -- ফিনফিনে --
নিখুঁত ধবধবে ।
ডন হুবানেরা, লোথারিওরা,
চেয়ে-দেখা রাজকুমারেরা,
আমাদের শ্রদ্ধা করে,
তাদের অভিনন্দন ও দীর্ঘশ্বাস :
যদিও লোকদেখানো, তাদের মুখবিকৃতি :
তারা নিজেদের নাকে আঘাত করে,
হাস্যকর আনন্দে
আমাদের বিলুপ্ত পোশাকে :
তবু আমাদের সরলতা
তাদের কল্পনাকে বিদ্রুপ করে
যারা হাওয়াকলের সঙ্গে লড়ে
যদিও অনেক সময়ে আমরা মনে করি
আমাদের হৃদয় দ্রুত স্পন্দিত হয়
চোরাগোপ্তা স্বপ্নে
এই কথা জেনে আমরাই ভবিষ্যতের
কামুকদের প্রেমিক ।
সান্ধ্য প্রেমসঙ্গীত
একজন মৃত মানুষের কন্ঠ হয়তো যেমন গান গাইবে
কবরের অতল থেকে,
আমার রক্ষিতা, সুরহীন আর কর্কশ, প্রতিধ্বনি করে
তোমার পানে, সে কন্ঠস্বর আমারই ।
তোমার আত্মাকে মেলে ধরো আর ধ্বনি শোনো
আমার ম্যান্ডোলিনের :
তোমার জন্য আমি এই গান লিখেছি, তোমার জন্য, খুঁজে পেয়েছি
এই নিষ্ঠুর, কোমল জিনিস ।
সমস্ত ছায়া থেকে বের করে এনে
আমি গাইবো তোমার সোনার আর স্ফটিকের চোখ,
তারপর তোমার বুকের লিথি, বৈতরণী
তোমার কালো চুলের নদীদের স্রোত ।
একজন মৃত মানুষের কন্ঠ হয়তো যেমন গান গাইবে
কবরের অতল থেকে
আমার রক্ষিতা, সুরহীন আর কর্কশ, প্রতিধ্বনি করে
তোমার পানে, সে কন্ঠস্বর আমারই ।
এরপর আমি গুণগান করব, সর্বোপরি
সেই আশীর্বাদপূত মাংসকে
যার বিলাসবহুল সুগন্ধ ডেকে আনে
অনিদ্রার বিপর্যয় ।
উপসংহার এই যে, আমি চুমুর কথা বলব
তোমার লাল ঠোঁটে,
আর আমার শহিদত্ব কেমন মিষ্টি,
--আমার দেবদূত ! -- আমার চাবুক !
তোমার আত্মাকে মেলে ধরো আর ধ্বনি শোনো
আমার ম্যাণ্ডোলিনের :
তোমার জন্য আমি এই গান লিখেছি, তোমার জন্য, খুঁজে পেয়েছি
এই নিষ্ঠুর, কোমল জিনিস ।
মূক অভিনয়
পিয়েরো, যিনি মোটেই ক্লিতান্দ্রের সমকক্ষ নন ( মলিয়ের জানতেন )
কোনো হইচই না করেই বোতল খালি করে ফেলতেন,
আর, চিরকাল যেমন ব্যবহারিক, আরম্ভ করতেন ময়দা মাখা ।
কাসেনদার, গলিপথের শেষে,
দু-এক ফোঁটা চোখের জল ফেলতেন যা কেউ দেখতে পেতো না
ওনার ভাইপোর জন্য, আজকে যে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত ।
সেই বজ্জাত হারলেকুইন তো দেখেছে
কোলোমবাইনের অপহরণ
আর চার বার ঘুরপাক ।
কোলোমবাইন স্বপ্ন দ্যাখে, আমাদের মতোই অবাক
হাওয়ার ভেতরে হৃদয় রয়েছে অনুভব করে
আর শোনো, মেয়েটির হৃদয়ে, স্বরের ছন্দ তৈরি হয় ।
আমাদের চলাফেরা
আকাশ এতো ম্লান আর গাছেরা এমন তন্বী
মনে হয় আমাদের উজ্বল পোশাক দেখে হাসছে
যা হালকা ভাসমান, একটু বেশি
নিস্পৃহ, ভূকম্পনের মতন ডানা ।
আর পুকুরে বলিরেখা আঁকে মলিন বাতাস,
আর সূর্যের আলোও নরম হয়ে আসে
রাস্তার দুধারের লেবুগাছের ছায়া
আমাদের করে তোলে, যেমনটা চায়, মর্মভেদী, নীল ।
সূক্ষ্ম প্রতারকদল, কমনীয় ছিনালেরা
কোমল হৃদয়, কিন্তু প্রতিশ্রুতিহীন,
আমাদের সঙ্গে আনন্দে কথা বলো আর অভিবাদন করো,
সব প্রেমিক-প্রেমিকারা তাদের পোষা প্রাণীকে লাই দ্যায়,
একটা হাত অনিবদ্যভাবে টোকা দেবে
এখন বা পরে, অদলবদল করবে
একটা চুমুর জন্য কড়ে আঙুলকে রেখে
ঠোঁটের কোনায়, আর যেহেতু ব্যাপারটা
নিরতিশয় অতিরিক্ত এবং যথেষ্ট কোপন,
তার জন্য শাস্তি পায় শুকনো চাউনি দিয়ে,
যা ঘটায় বিষমতা, ঘটনাক্রমে, আলতো-খোলা ঠোঁট
ক্ষমাশীলতার নাটুকে মহলা চালায় ।
নিষ্পাপ মানুষেরা
দীর্ঘ পোশাকের সঙ্গে লড়েছে হিল-তোলা জুতো,
যাতে, মৃদুমন্দ হাওয়া আর উৎরাই প্রশ্ন তোলে,
কনুই কখনো-বা আমাদের মুগ্ধ করতে আভাসিত হয়,
আহ, কালহরণ ! -- প্রিয় মূর্খতা !
ঈর্ষান্বিত কীট হুল ফোটায় অনেকসময়ে
শাখার তলায় সুন্দরীদের বিক্ষুব্ধ গলা,
আচমকা ঝলকানিতে উঁকি দেয় শ্বেতাঙ্গিনী গ্রীবা
তোমার কচি-চোখের বুনো চাউনির উৎসব ।
সন্ধ্যা নামে, দ্বর্থ্যক হেমন্তের সন্ধ্যা :
সুন্দরীরা, স্বপ্নালিনীরা, যারা আমাদের কাঁধে হেলান দিয়েছে,
বলেছে ফিসফিসে শব্দ, কতো ছলাকলা, এমন কমনীয়,
আমাদের আত্মা রয়ে গেছে স্পন্দনে আর গানে-গানে ।
যুবতীর অনুচরগণ
জরিতে বিভূষিত একটি বাঁদর
খেলা দেখায় তিড়িং-বিড়িং নাচে কেননা মেয়েটি
যে ঘোরাচ্ছে রুমালের কিনার
কবজি পর্যন্ত দস্তানা পরা তার হাতে,
তখন এক কালো কেনা গোলাম লাল রঙের পোশাকে
দাঁড় করিয়ে রাখে গাড়ি, এক হাতের দূরত্বে,
মেয়েটির গুরুভার পোশাক, অভিপ্রায়
লক্ষ রাখার যাতে ভাঁজগুলো নষ্ট না হয় ।
বাঁদরটা কখনও চোখ সরায় না
যুবতীর নরম শাদা গলদেশ থেকে ।
প্রচুর ঐশ্বর্য যার বৈভবী টীকা
পুরস্কাররুপে কোনো দেবতার নগ্ন ধড় চায় ।
ক্রীতদাস কখনও-বা ওপরে ওঠাবে,
বজ্জাত, যতোটা সে চায় তার বেশি,
নিজের মহার্ঘ ভার, যাতে সে
রাতে যা স্বপ্নে দেখে তা-ই দেখতে পায় ;
তবু মনে হয় যুবতীটি এখনও অবিদিত
যখন সে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছে
দাম্ভিক অনুমোদন কেমন দেখায়
তার পরিচিত প্রাণীর জ্বলন্ত চোখে ।
সমুদ্রের ঝিনুকগুলো
প্রতিটি ঝিনুক, আবরণে ঢাকা, আমরা দেখি,
যেখানে আমরা প্রেমের উদ্দেশ্য পূরণ করতে চেয়েছি সেই গুহায়,
তার নিজের বিশেষত্ব আছে ।
একটির আছে আত্মার বেগুনি রঙ,
আমাদের, রক্তের ডাকাত যা হৃদয়কে ভোগদখল করে
তখন আমি জ্বলি আর তুমি দাউদাউ করো, তপ্ত কয়লার মতো ।
ঐ আরেক যা তোমার অবসন্নতাকে প্রভাবিত করে,
তোমার বিবর্ণতা, তোমার ক্লান্ত গড়ন
আমার দৃষ্টিবিদ্রুপে ক্রুদ্ধ :
এই আরেকটা নকল করে স্নিগ্ধতা
তোমার কানের, আর এটা আমি দেখি
তোমার গোলাপি গ্রীবা, কতো সুডৌল আর উষ্ণ :
কিন্তু একটা, তাদের মধ্যে একটা, আমাকে ক্লিষ্ট করেছে ।
জড়পুতুলেরা
স্কারামোচে আর পুলসিনেলা,
দুষ্টুমি করার জন্য একত্রিত হল
অঙ্গভঙ্গী করে, কালো চাঁদের দিকে ।
তখন সবচেয়ে ভালো ডাক্তার
লোকটা বোলোনাবাসী, ধীরে জড়ো করে
ঘাসের গর্ভ থেকে যতো জড়িবুটি ।
কিন্তু কুটিল-চোখ ওর মেয়ে,
লুকিয়ে কূঞ্জবনে,
অর্ধেক উলঙ্গ, পিছলায়, খুঁজে ফেরে
নিজের স্পেনিয় জলদস্যুকে :
মিষ্টি গলার এক পাপিয়া
দুর্দশা ঘোষণা করে তার ।
জাহাজে
মেষপালকের নক্ষত্র, শিহরিত,
কাণ্ডারী, অন্ধকার জলে,
নিজের ট্রাউজারের ভেতরে চায় আগুন ।
এখনই সেই সময়, মহাশয়্গণ, কিংবা আর কখনও নয়,
বেপরোয়া হবার জন্য, আর তুমি আবিষ্কার করবে
আমার হাতগুলো, এখন থেকে, সর্বত্র !
রোমের পুরাণের আতিস, রাজকুমার, নিজের গিটারে
টুংটাং তোলে, শীতল মায়াবিনী ক্লোরিস
নজর মেলে দ্যাখে, আর তাও নচ্ছার ।
যাজক স্বীকৃতি শোনে সাপের রানি বেচারি এগলের,
আর সেই ভাইকাউন্ট, বিড়ম্বনায়,
ফসলখেতের রাজকুমার, নিজের হৃদয় বিলিয়ে দিয়েছে ।
ইতিমধ্যে চাঁদ ঝরিয়ে ফেলেছে নিজের দীপ্তি
জাহাজের তলাকার সংক্ষিপ্ত ধাবনে
মজায় নাচতে-নাচতে স্বপ্নালু স্রোতে ।
ফন : ছাগলের শিং ও লেজযুক্ত রোমের দেবতা
পোড়া মাটির এক প্রাচীন ফন
বল খেলার সবুজ মাঠে
হাসে, নিঃসন্দেহে সঙ্কেত দিয়ে,
এই সুন্দর সময়ের দুঃখি অবশেষ,
যা আমাকে আর তোমাকে নিয়ে চলেছে
অজর হতাশার তীর্থে,
এই সময়ে যার ফুরিয়ে যাওয়ার
ঘুর্ণিতে বেজে ওঠে তাম্বুরা ।
ম্যাণ্ডোলিন
সান্ধ্য প্রেমসঙ্গীতের বাদকেরা
আর তাদের সুসজ্জিত শ্রোতারা
বিরস মন্তব্য চালাচালি করে, গুঞ্জরিত
গাছের শাখার তলায় বসে ।
এখানে রয়েছে ট্রিসিস আর অমিনতা
আর শাশ্বত ক্লিতান্দের,
আর দামিস যে নিষ্ঠুরদের অনেকের
স্হান নেয়, বহু গান যা বেশ কমনীয় ।
রেশমের পোশাক ছোটো করে কাটা,
তাদের দীর্ঘ আলখাল্লার চাদর,
তাদের লালিত্য, খোশমেজাজ চাতুরি,
আর তাদের মোলায়েম নীল ছায়া,
ভাবাবেশে আবর্তিত হয়
গোলাপি ও ধূসর চাঁদ থেকে পাওয়া
যখন দমকা হাওয়ার ঝাপটায়
ম্যাণ্ডোলিনের ঝঙ্কার মিলিয়ে যেতে থাকে ।
কোলোমবাইন
মূর্খ লিয়েনডার,
পিয়েরোও লাফাচ্ছিল
মাছির মতন
আর বনে ঝাঁপ খাচ্ছিল,
টুপি-পরা কাসেনদার
মঠের সন্ন্যাসীর মতো,
আর তারপর সেই সঙ,
পাপের ধড়িবাজ
উদ্ভট,
পাগলের পোশাকে,
চোখ তার জ্বলছিল,
ঠাকতে পারেনি,
সা, রে, গা, মা, পা -
সবাই ছড়িয়ে আর দূরে
হাসতে হাসতে চলে গেল
মেয়েটির জন্য গাইতে-গাইতে, নাচতে-নাচতে
সেই ছোট্ট তোরণ
চমৎকার
চোখ যার লম্পট
সবুজ বা আরও খারাপ
বিড়ালের মতো,
ওর সৌন্দর্যে কাঁদো কেননা,
‘আহ, তোমার থাবা কোথায় রেখেছো
খেয়াল করো !’
-- সবসময় যাবার জন্য ব্যস্ত !
নিয়তির নক্ষত্র যা ভেসে বেড়ায়
দ্রুত,
ওহ, বলো, সেই বিষয়ে
নিষ্ঠুর কিংবা অস্বস্তিকর লোকজন,
অভাবনীয় বিপর্যয়
এই নির্দয়ী ছিনাল,
আলতো করে স্কার্ট তোলে
তার দলবল,
মেয়েটির চুলে গোলাপ,
ওই দিকে এগিয়ে যায়,
মেয়েটির প্রতারণার শিকার ?
কিউপিড নিপাতিত
গত রাতের বাতাস দেখলো কিউপিড নিপাতিত,
পার্কের সবচেয়ে রহস্যময় কোনে, কে
ছলনাময় হাসি হেসে নিজের ধনুক বেঁকাবে,
তার মুখভঙ্গী আমাদের তেমনই দিবাস্বপ্ন দেখতে বলছে !
গত রাতের বাতাস ওকে ঠেলে ফেলে দিলো ! শ্বেতপাথর
ভোরের নিঃশ্বাসে চুরমার । দেখতে খারাপ লাগে
ওর বেদি, তাতে ভাস্করের নেম এক রহস্য,
কুঞ্জবনের ছায়ায় তা দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল না ।
ওহ, ফাঁকা বেদিটা দেখে মন খারাপ হয়
পুরোটা খালি ! আর বিষাদ ভাবছিল প্রবেশ করবে
আমার স্বপ্নে চলাফেরা করবে, যেখানে গভীর মর্মবেদনা
এক ভবিষ্যত-নিঃসঙ্গতা আর নিয়তিনির্দিষ্টতার ডাক পাড়ে ।
ওহ, এটা ভালো নয় ! -- আর তুমি তা অনুভব করো, হ্যাঁ, তুমিও,
দৃশ্য দিয়ে আবেগপীড়িত, যদিও তোমার ইতিউতি চোখ
সোনালী আর রক্তিম প্রজাপতির পুতুল নিয়ে খেলে
পথের ধারে ফেলে দেয়া জঞ্জালের গাদা ঘেঁটে ।
ভাবপ্রবণ কথোপকথন
পুরোনো ফাঁকা পার্কের জমাটবাঁধ কাচ দিয়ে
দুটি কালো ছায়া সম্প্রতি চলে গেলো ।
ওদের ঠোঁট ছিল ঢিলেঢালা, চোখ ছিল ঝাপসা,
শোনা যাচ্ছিল না ওরা কী যে বলছিল ।
পুরোনো ফাঁকা পার্কের জমাটবাঁধা কাচ দিয়ে
অতীতকে আহ্বান করল দুটি ভুতুড়ে আদল ।
‘তোমার কি মনে আছে আমাদের বিগত আহ্লাদ ?’
‘কেন তুমি আমায় স্মৃতি খুঁড়ে আনতে বলছ ?’
‘তোমার হৃদয় কি এখনও শুধু আমার নামে স্পন্দিত হয় ?’
‘তুমি কি সব সময় আমার আত্মাকে স্বপ্নতে দ্যাখো ?’ - ‘আহ, না’ -।
‘ওহ সেই অবর্ণনীয় রহস্যময় সুন্দর দিনগুলো,
যখন আমাদের মুখের মিলন ঘটত !’ -- ‘আহ হ্যাঁ, সম্ভবত ।’
‘কতো নীল ছিল, আকাশ, কতো উঁচু আমাদের আশা !’
‘বিদায় নিয়েছে আশা, বিজয়ী, অন্ধকার ঢালে ।’
ওরা দুজনে সেখানে পায়চারি করছিল, বুনো জড়িবুটির মাঝে,
আর তাদের কথাবার্তা কেবল শুনছিল রাত ।
 কলিম খান | 122.179.172.247 | ২৪ আগস্ট ২০২১ ১৯:২৯734901
কলিম খান | 122.179.172.247 | ২৪ আগস্ট ২০২১ ১৯:২৯734901এক রাজদ্রোহী রাজকুমারের কাহিনি : কলিম খান
প্রথম পর্ব : ষড়যন্ত্র : মারণ
( কোরাণ ও গীতা : পুনঃপাঠ )
মহম্মদ কহিলেন : হে আবুবক্কর ! মদিনা হইতে এই বিশাল সৈন্যবাহিনী লইয়া যে উদ্দেশ্যে হেথায় আসিয়াছি, তাহা বুঝি আর সফল হইল না । দেখো, সন্মুখসমরে আজ আমারই কোরেশ বংশের বংশজগণ । আর দেখো, উভয় সেনার মধ্যে আমারই পিতৃব্যগণ পিতামহগণ আচার্য্যগণ মাতুলগণ ভাতৃগণ পুত্রগণ পৌত্রগণ মিত্রগণ শ্বশুরগণ সুহৃদগণ অবস্হান করিতেছেন । আমি কাহাকে হত্যা করিব ? হে আবুবক্কর ! যুদ্ধেচ্ছু এই সকল স্বজনদিগকে সন্মুখে অবস্হিত দেখিয়া আমার শরীর অবসন্ন হইতেছে এবং মুখ শুষ্ক হইতেছে । ইহা সত্য যে, ৩৬০টি প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়া ইহারা যুগযুগান্ত ধরিয়া আরববাসীগণকে প্রতারিত করিতেছে, আর ওই প্রতীকগুলির সাহায্যে পুরাতন জীবনব্যবস্হায় তাহাদিগকে মোহগ্রস্হ করিয়া রাখিয়াছে, তাহাদের ধনসম্পদ ভোগ করিতেছে । ইহাও সত্য যে, আমি এই বংশেরই এক কনিষ্ঠতম ও অবহেলিত অবক্ষিপ্ত উত্তরাধিকারী, এক দুয়ো-রাজকুমার । তথাপি এক্ষণে ইহাদিগকে সমরাঙ্গনে সন্মুখস্হ দেখিয়া আমার হস্তপদ অবসন্ন হইয়া আসিতেছে ।
আবুবক্কর কহিলেন : অয় মুহম্মদ ! এই সঙ্কট সময়ে স্বর্গহানিকর অকীর্তিকর তোমার এই মোহ কোথা হইতে উপস্হিত হইল ? এ যুদ্ধ স্বার্থপ্রণোদিত নহে, ইহা জেহাদ, ধর্মযুদ্ধ । হে পরন্তপ ! তুচ্ছ হৃদয়ের দুর্বলতা ত্যাগ করিয়া যুদ্ধার্থে উথ্থিত হও ! জেহাদ অপেক্ষা ইমানদার মোমিনের পক্ষে শ্রেয়ঃ আর কিছুই নাই । হে ধনঞ্জয় ! এই যুদ্ধ জগৎপিতার নিয়মে স্বয়ং উপস্হিত হইয়াছে । ইহা আমাদের নিমিত্ত জন্নাতের দ্বার উন্মুক্ত করিবে । অতএব যুদ্ধার্থে উথ্থিত হও । অন্যথায় মহারথগণ মনে করিবেন, তুমি ভয়বশত যুদ্ধে বিরত হইতেছ, দয়াবশত নহে । সুতরাং যাহারা তোমাকে বহু সন্মান করেন, তাহাদিগের নিকট তুমি লঘুতাপ্রাপ্ত হইবে । তোমার শত্রুরাও তোমার সামর্থ্যের নিন্দা করিয়া অনেক অবাচ্য কথা বলিবে । তাহা অপেক্ষা অধিক দুঃখকর আর কী আছে ? এক হস্তে অধর্মের বিনাশ ও অপর হস্তে ধর্মের প্রতিষ্ঠা নিমিত্ত তুমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। ধর্মভ্রষ্টদিগকে হত্যা করিতে দ্বিধা কিসের ? সুতরাং হে সব্যসাচী, যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া উথ্থান করো।
সব্যসাচী কহিলেন : ইহা সত্য যে, ইহারা ধর্মভ্রষ্ট । এই কৌরবগণ আমাদিগের ন্যায় ইক্ষাকু বংশজ হইলেও ইহারা ধর্মের অমর্যাদা করিয়াছে । প্রজাপালন বিষয়ে ইহাদিগের দুঃশাসনের কোনও সীমা নাই । ইহাও সত্য যে, আমরা এই বংশেরই অবহেলিত অবক্ষিপ্ত উত্তরাধিকারী, এই রাজবংশের দুয়ো-রাজকুমার এবং ইহারা আমাদিগকে আশৈশব প্রবঞ্চনা করিয়া আসিতেছে, সাধারণ প্রজাদিগের তো কথাই নাই । সেই হেতু ধর্মপ্রতিষ্ঠার স্বার্থেই ইহাদিগকে ক্ষমতাচ্যুত করা প্রয়োজন । কিন্তু এতৎসত্বেও, স্বজন ও গুরুজনদিগকে বধ করিয়া কীরূপে প্রাণধারণ করিব, এইরূপ চিন্তাপ্রযুক্ত হইয়া চিত্তের দীনতায় আমি অভিভূত হইতেছি । প্রকৃত ধর্ম কী, এ বিষয়ে আমার চিত্ত বিমূঢ় হইতেছে । ধর্মপ্রতিষ্ঠার নিমিত্ত এ আমি কাহার হত্যাকারী হইতে চলিয়াছি ? অতএব হে কৃষ্ণ ! যাহাতে শুভ হয়, আমাকে নিশ্চিত করিয়া তাহা বলো !
শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন : প্রকৃতপক্ষে তুমি কাহারও হত্যাকারী নহ। স্বজন বা গুরুজন যাহাই হউন, যাহারা অন্যায়কারী, প্রজাবৃন্দের প্রতি নির্দয়, অচলায়তন রূপে সমাজের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাঁহারা ধর্মভ্রষ্ট হইয়াছেন । কাল সমুপস্হিত হইলে স্বয়ং শিব ধর্মভ্রষ্টদিগের মহিমাহরণ করিয়া তাহাদিগকে হনন করিয়া রাখেন । এক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে, তুমি নিমিত্তমাত্র । সত্যের জন্য, ধর্মের জন্য, স্বজন ও গুরুজনদিগের উপর বাণনিক্ষেপ করিলে কদাচ অধর্ম হয় না। সুতরাং, তুমি নিঃসংশয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও । যাহারা সত্যের নিমিত্ত ধর্মের নিমিত্ত পিতৃব্য ও পিতামহ প্রভৃতি স্বজনগণকে নিকেশ করিতে দ্বিধা করেন না, তাহারাই প্রকৃত ধার্মিক । ইতিহাস তাহার সাক্ষী । অতএব, হে পাশুপতধারী মোমিন ! হে দুয়ো-রাজকুমার ! হে বংশদ্রোহী! তুমি যুদ্ধ করো ।
দ্বিতীয় পর্ব : ষড়যন্ত্র : মোহন
( দেবীপুরাণ : পুনঃপাঠ )
ঋষিগণ কহিলেন : হে পণ্ডিতপ্রবর ! যথার্থ পথপ্রদর্শক নেতাই গুরুপদবাচ্য । তাঁহাকে সম্যকরূপে অবগত না-হইয়া তাঁহার অনুসরণ করা উচিত নহে । ইহা জানিয়াও অসুরগণ কী প্রকারে ভুল নেতৃত্বের দ্বারা প্রবঞ্চিত হইলেন, এক্ষণে সে বিষয়ে আমাদিগের কৌতূহল নিবারুণ করুন ।
বৈশ্যম্পায়ন কহিলেন : বৃহস্পতি ও শুক্রাচার্য উভয়েই ভৃগুর সন্তান হইলেও তাঁহাদের অভিমত ভিন্ন ছিল । সেই কারণে সুরাসুর সংগ্রামে তাঁহারা যথাক্রমে দেবতা ও অসুরগণের পরামর্শদাতারূপে তাহাদের গুরুর আসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন ।
একদা অসুরগণকে সংযত থাকিতে বলিয়া শুক্রাচার্য্য তপস্যার উদ্দেশ্যে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিলেন । একথা জানিতে পারিয়া দেবগুরু বৃহস্পতি স্বল্পকাল অতিবাহিত হইলে শুক্রাচার্য্যের রূপ ধারণপূর্বক তথায় উপস্হিত হইলেন । তাঁহাকে সমুপস্হিত দেখিয়া অসুরগণ তাঁহাদিগের গুরুদেব প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন, এইরূপ প্রত্যয় করিল এবং তাঁহাকে পাদ্য অর্ঘ্য দানে যথাবিহিত সন্মান প্রদর্শনপূর্বক তাঁহার উপদেশের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল । অনন্তর শুক্রাচার্য্যরূপী বৃহস্পতি তাহাদিগকে বলিলেন, বৈরিতা কুলক্ষয়ের কারণ । বৈরিতার কারণ বাসনা, অতএব বাসনা পরিত্যাগ করো । বাসনা না থাকিলে কেহই তোমাদিগকে বশীভূত করিতে পারিবে না । অতএব তোমরা বাসনামুক্ত হও, মস্তকমুণ্ডনকরতঃ গৈরিক বস্ত্র ধারণ করিয়া আচারনিষ্ঠ হও । আচারনিষ্ঠগণকে দেবতাও জয় করিতে পারিবে না । গুরুদেবের আদেশ শিরোধার্য করিয়া অসুরগণ তাহাই করিতে লাগিলেন । ইহার ফলে তাহাদিগের হৃদয় হইতে অসূয়াভাব ক্রমে তিরোহিত হইতে লাগিল ।
ইট্যবসরে, দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য তাঁহার তপস্যা সমাপনান্তে তথায় সমাগত হইলেন । দেবগুরু বৃহস্পতিকে অসুরগণের গুরুপদে অধিষ্ঠিত দেখিয়া তিনি যারপরনাই বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া অসুরগণকে কহিলেন--- এ কাহাকে তোমরা আমার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছ ? ইনি যে দেবগুরু বৃহস্পতি, তাহা কি তোমরা উপলবদ্ধি করিতে পারো নাই ? তোমাদিগকে বিপথগামী করিবার জন্য আমার অনুপস্হিতির সুযোগ গ্রহণ করিয়া এ প্রবঞ্চক তোমাদিগের সহিত প্রতারণা করিয়াছে । ইনি আমাদিগের ন্যায় স্বর্গদ্রোহী নহেন । তোমাদের নেতার আসন গ্রহণ করিয়া তোমাদের সংগ্রামকে ধ্বংস করাই এই প্রতারকের একমাত্র উদ্দেশ্য ।
ইহা শুনিয়া শুক্রাচার্য্যরূপী বৃহস্পতি কহিলেন : হে অসুরগণ! অবধান করো ! আমার উপদেশে তোমরা অজেয় হইতে চলিয়াছ দেখিয়া দেবগুরু বৃহস্পতি তোমাদিগকে প্রতারণা করিবার উদ্দেশ্যে এক্ষণে আমার রূপ ধারণ করিয়া তোমাদিগের সন্মুখে উপস্হিত হইয়াছেন । ইনি দেবগুরু বৃহস্পতি । অবিলম্বে ইহার মুখে চুনকালি দিয়া গর্দভের পৃষ্ঠে আরোহন করাইয়া পশ্চাতে হ্ল্লা লাগাইয়া দাও এবং বিতাড়ন করো । অসুরগণ তাহাই করিল ।
কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে, অসুরগণ একদিন হৃদয়ঙ্গম করিল, তাহারা প্রবঞ্চিত হইয়াছে । কিন্তু তখন তাহাদিগের আর কিছুই করিবার রহিল না ।
এইভাবে অসুরগণ ছদ্ম-দেবদ্রোহীকে তাহাদের নেতারূপে বরণ করিয়া মোহগ্রস্ত হইয়াছিল এবং সম্পূর্ণরূপে প্রবঞ্চিত হইয়াছিল ।
তৃতীয় পর্ব : ষড়যন্ত্র : স্তম্ভন
( মুক্তধারা : পুনঃপাঠ )
এক যে ছিল রাজা । তার ছিল দুই রানি, সুয়োরানি আর দুয়োরানি। সুয়োরানি সুখে থাকে রাজপ্রাসাদে আর দুয়োরানি থাকে বনের প্রান্তে, ছোট নদীর ধারে, কুঁড়ে ঘরে। দুয়োরানির ছেলে সেই নদীতে নৌকাবায় । পারানির কড়িতে তাদের দিন কাটে । কিন্তু একদিন তার সাধের নদী শুকিয়ে গেল । কারণ, দেশের রাজ-বিভূতি বাঁধ বেঁধেছেন । কেবল জলধারা নয়, ঈশ্বরের করুণার সকল ধারার সামনেই বাঁধ বেঁধেছেন তাঁরা । লোকে বিস্বাসই করতে পারল না যে, দেবতা তাদের যে জল দিয়েছেন, কোনও মানুষ তা বন্ধ করতে পারে । কিন্তু বন্ধ হল, করুণাধারার সব শাখাই ক্রমশ শুকোতে লাগল, আর প্রজাদের জীবন উঠল অতীষ্ঠ হয়ে । এদিকে একদিন দুয়োরানির ছেলে জানতে পারল সে রাজপুত্তুর । সে গেল রাজার কাছে, বললে, রাজপুত্রের অধিকার চাইনে । কেবল ঈশ্বরের করুণাধারার সামনে দেয়া তোমাদের ওই বাঁধগুলো খুলে দাও, এই প্রার্থনা । শুনে সুয়ো-রাজপুত্রেরা অবাক হলো । তারা সেপাই ডাকল, সান্ত্রী ডাকল । ঘাড়ধাক্কা দিয়ে রাজবাড়ি থেকে বার করে ছুঁড়ে ফেলে দিলো রাস্তায় ।
ধুলো ঝেড়ে সে উঠে দাঁড়াল । তারপর গেল শিবতরাইয়ের প্রজাদের কাছে । সেখানে গিয়ে সে অবাক হয়ে গেল । সে দেখল, ধনঞ্জয় বৈরাগীর ছদ্মবেশে সুয়োরানির এক ছেলে । আর, তার পেছনে শিবতরাইয়ের মানুষগুলো চলেছে মুক্তধারার বাঁধ ভাঙতে । তখন সেই দুয়ো-রাজকুমার সবাইকে ডেকে বলতে লাগল, ওই বৈরাগী আসল বৈরাগী নয়, ও তো ছদ্মবেশী সুয়ো-রাজকুমার, ও তোমাদের ঠকাবে । এক নদীর মুখেই ওরা বাঁধ বাঁধেনি । সর্বহারার মুখেই ওরা বাঁধ বেঁধেছে । সেগুলি ভাঙতে হলে, তাদের রহস্য জানতে হবে । সেসব আমি জেনে এসেছি । আমার কথা শোনো । কিন্তু দু'চারজন আধপাগলা ছাড়া কেউ তার কথায় কান দিল না ।
কথাটা গেল মিথ্যে-বৈরাগীর কানে, সে বললে -- ওটা বদ্ধ পাগল । ছন্নছাড়া । খেতে পায়না, হাংরি, তাই মিথ্যে কথা বলে । ওর মুখে চুনকালি মাখিয়ে গর্দভের পিঠে চড়িয়ে পিছনে ভিড়ের হল্লা লাগিয়ে দাও । মজা পেয়ে প্রজারা তাই করলে ।
এরপর গাধার পিঠে সওয়ার দুয়ো-রাজকুমারের আর কিছুই করার রইলো না । তাই সে কেবল চিৎকার করে । চিৎকারের জন্য চিৎকার । চিৎকারের ভিতরে চিৎকার । চিৎকার করতে করতে একদিন সে বিস্মৃতিলোকে চলে গেলো ।
তারপর অনেকদিন কেটে গেলে, শিবতরাইয়ের প্রজারা বুঝল তারা ঠকেছে । অতএব, তারা খোঁজ করতে লাগল সেই দুয়ো-রাজকুমারের, যে জানত সব বাঁধের রহস্য । কিন্তু তাকে আর পাওয়া গেল না । তখন যে আধপাগলারা সেসময় তার কথা শুনেছিল মন দিয়ে, তাদেরকে ধরা হলো । বাঁধ ভাঙার রহস্য ওই আধপাগলারা দুয়ো-রাজকুমারের কাছ থেকে জেনে-বুঝে নিয়েছিল কি না, সেটা জানার জন্য । কিন্তু কেউই সেসব কথা ঠিকঠাক বলতে পারল না ।
রাজপ্রাসাদ থেকেও দুয়ো-রাজকুমারের খোঁজখবর করা হলো । কিন্তু তাকে পাওয়া গেল না, পাওয়া গেল তার গাধাটাকে । তাকেই নিয়ে এসে ফুলমালা দিয়ে চন্দনের টিপ পরিয়ে রাজসভায় আনা হলো । রাজা সেই গাধাটাকেই শিরোপা দিলেন আর রাজপুরোহিত দিলেন আশীর্বাদ । সবাই বলে উঠল -- সাধু, সাধু !
চতুর্থ পর্ব : ষড়যন্ত্র : বিদ্বেষণ
( অভিচারতন্ত্র : পুনঃপাঠ )
মানুষের উপর মানুষের চড়ে বসাকে বলা হয় 'অভিচরণ' বা 'অভিচার' । আদিকালে সর্বপ্রথম যে-পদ্ধতির সাহায্যে এই কর্মটি করা হতো, তাকে বলা হতো 'শ্যেনযাগাদি' অর্থাৎ অন্য গোষ্ঠীর লোকেদের উপর দলবদ্ধ লুঠতরাজ বা ছিনতাই । তবে সে সবই ছিল সাময়িক । তার সাহায্যে বহুকালের জন্য বা চিরকালের জন্য কারও উপর চেপে বসা যেত না । সেই উদ্দেশ্যে একদিন ভারতবর্ষ আবিষ্কার করে এক অভিনব প্রক্রিয়া ---'মূলনিখনন ও পদধূলিগ্রহণ'। এই প্রক্রিয়া প্রয়োগ করে সমাজের স্বাভাবিক জ্ঞানপ্রবাহের উপর বাঁধ বাঁধা হয় ও বৈদিকযুগের সূত্রপাত করা হয় । এটিই পৃথিবীর প্রথম বাঁধ ও আদি বাঁধ । ঈশ্বরের করুণার অন্যান্য ধারাগুলিকে বাঁধ বেঁধে নিয়ন্ত্রণ করার কথা তখনও ভাবা হয়নি ।
তা সে যাই হোক, সেই 'মূলনিখনন ও পদধূলিগ্রহণ' উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছি বলে এখনও আমরা 'বড়ো শত্রুকে উঁচু পিঁড়ি' দিই ; যার সর্বনাশ করা দরকার তার মূর্তি গড়ে পূজা করি ও তার নীতি অমান্য করি এবং এভাবেই আমরা আজও শিব রাম গান্ধী মার্কস রবীন্দ্রনাথের পূজা করি ও তাঁদের নীতি অমান্য করে থাকি।
দুষমনকে 'পূজা করে মেরে ফেলার' এই বৈদিক নীতির বিপরীতে একসময় তান্ত্রিক নীতিরও জন্ম হয় এই ভারতবর্ষেই । 'নিয়ন্ত্রণসাধন'কে তখন বলা হতিও যন্ত্র, যা দিয়ে অন্যদের নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা চালানো হতো, ঘাড়ের উপর চেপে বসা ক্ষমতাকে উৎখাত করার চেষ্টা চালানো হতো । তান্ত্রিকেরা শত্রুকে নিয়ন্ত্রণ করার উপায় হিসেবে ছয় রকম 'নিয়ন্ত্রণসাধন' বা যন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন--- মারণ, মোহন, স্তম্ভন ( শত্রুকে স্ট্যাগন্যান্ট করে দেয়া ), বিদ্বেষণ ( ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল ), উচ্চাটন ( স্বদেশভ্রংশন বা শত্রুকে তার কনটেক্সট থেকে উৎখাত করে দেয়া ) ও বশীকরণ । এই যন্ত্রগুলি প্রধানত বাঁধ ভাঙার কাজেই ব্যবহৃত হতো । বৈদিকদের পূজা করে মেরে ফেলার বিপরীতে তান্ত্রিকেরা এই ছয় রকম যন্ত্র ব্যবহার করতেন বলে, বৈদিকপন্হীদের কালচারে এই 'ষড়যন্ত্র' ঘৃণ্য ও নিন্দাজনক হয়ে যায় এবং আধুনিক যুগে পৌঁছে পরিণত হয় 'কন্সপিরেসি'তে, যদিও তান্ত্রিক কালচারে 'ষড়যন্ত্র' যথারীতি প্রশংসাযোগ্য ও গৌরবজনক হয়েই থেকে যায় । অর্থাৎ কিনা, ভারতের তান্ত্রিক ঐতিহ্য অনুসারে ষড়যন্ত্রের প্রয়োগ অত্যন্ত ভালো কাজ এবং তা আদৌ কন্সপিরেসি নয়।
তবে নিয়ন্ত্রণসাধনের এই চর্চা এখানেই থেমে থাকেনি । যুগ বহুদূর এগিয়ে চলে এসেছে, যন্ত্রকে করে তোলা হয়েছে 'মোস্ট সফিসটিকেটেড', ক্ষমতা হয়েছে নিরঙ্কুশ । শাসক ও বিদ্রোহীর হাতে ওইসকল যন্ত্রের বিপুল বিকাশ ঘটেছে । বিকাশ ঘটেছে শাসক এবং বিদ্রোহীরও । এখন শাসকের বহু রূপ, বহু সুয়ো ; বিদ্রোহীরও বহু রূপ, বহু দুয়ো । বহু ক্ষেত্রে শাসকই বিদ্রোহীর পোশাক পরে নেয়, কোনও কোনও দুয়ো ভুয়ো-বিদ্রোহী হয়ে সুয়োর দলে ভিড়ে যায় । তাছাড়া, এখন বাঁধের সংখ্যাও প্রচুর, যত ধারা ততো বাঁধ, বাঁধের নিচে বাঁধ, উপরে বাঁধ, সাপোর্টিং বাঁধ, কতো কী ! এমনকি লোকদেখানো মিথ্যে বাঁধও রয়েছে, বিদ্রোহী জনগণের আক্রোশ যার উপর ফেটে পড়ে বেরিয়ে যেতে পারবে, ডায়লুট ও ডাইভার্টেড হয়ে যেতে পারবে, অথচ প্রকৃত বাঁধটা থেকে যাবে অক্ষত ।
আরও আছে, এখনকার প্রতিটি বাঁধের পাথরপ্রতিমার রূপগুণও ভিন্ন ভিন্ন, পৃথক পৃথক স্পেশালিস্ট বা দক্ষ বিভূতিদের দিয়ে বানানো । এসব বাঁধ ভাঙতে গেলে বিদ্রোহীদেরও ভিন্ন ভিন্ন শাখার স্পেশালিস্ট হতে হয়, দক্ষ হতে হয়, অনেক তপজপ করতে হয় । কেননা এমন ব্যবস্হা করে রাখা হয়েছে যাতে কৃষিবিজ্ঞানী সাংস্কৃতিক বাঁধের রহস্য জানতে না পারেন, জীববিজ্ঞানী রাজনৈতিক বাঁধের রহস্য জানতে না পারেন...ইত্যাদি ইত্যাদি। কারণ প্রতিটি বাঁধই সেই সেই বিষয়ের প্রতীকের পাথরপ্রতিমা দিয়ে গড়া । তাই, একালে একজন দুয়ো-রাজকুমারে কিছুই হবার নয় । যতোগুলি বাঁধ, বলতে গেলে ততোজন দক্ষ দুয়ো-রাজকুমার লাগে সেগুলি ভাঙবার আয়োজন করতে।
তাই একালে দুয়ো-রাজকুমারের সংখ্যাও খুব কম নয় । এর ভিতর আবার জালি দুয়ো-রাজকুমার তো রয়েছেই । তার ওপর, কখনও বা কোনও কোনও দক্ষ দুয়ো-রাজকুমারকে রাতারাতি ফুটপাত বদল করতেও দেখা যায় । অবশ্য তার জন্য তাদের ফ্ল্যাট নিতে হয় 'কনখল'-এ । 'কনখল' সেই বিখ্যাত কমপ্লেক্স, যেখানে দাঁড়িয়ে আদি দক্ষ বলেছিল, 'কৌ ন খল অর্থাৎ কে খল নহে ? সব্বাই খল । অতএব আমিও কেন খল হবো না ?' এই বলে, সেও খল হয়ে যায় । সেই জন্য, সেই ভিত্তিভূমির নাম হয়ে যায় 'কনখল' । এলাকার ফুটপাত-বদল-পারদর্শী দক্ষেরা সেই কমপ্লেক্সে আশ্রয় নিয়ে ঘোষণা করে, 'কে খল নহে ? সব্বাই খল । কেউ কথা রাখেনি । অতএব আমিও কথা রাখব না ।' ---এই বলে তারা সুযোগ পাওয়া মাত্রই সুয়ো-রাজকুমারের দলে ভিড়ে যায় । তাই প্রকৃত বিদ্রোহী দুয়ো-রাজকুমারকে চিনতে পারা এযুগের এক কঠিন সমস্যা ।
আবার বাঁ৭ ভাঙার ক্ষেত্রেও রয়েছে সমস্যা । পালটা প্রতীকের পাথরপ্রতিমা না বসিয়ে বাঁধের বর্তমান পাথরকে সরানোর কোনও উপায় রাখা হয়নি । আর সেটা করতে গেলেই নতুন প্রতীকের বাঁধ নির্মিত হয়েযায় । ফলে, যে ভাঙতে আসে, দেখা যায়, পাকে চক্রে সে আগের বাঁধ ভেঙে তার স্হানে নতুন আর একটা বাঁধ বেঁধে ফেলেছে নিজের অগোচরেই ।
এই সমস্যার মুখোমুখি হয়ে, সাম্প্রতিক কালের অধুনান্তিক ( পোস্টমডার্ন ) তান্ত্রিক বিদ্রোহীরা একটি অভিনব পন্হা উদ্ভাবন করেছেন । বাঁধের উৎখাতযোগ্য পাথরপ্রতিমাকে অত্যন্ত স্বল্পায়ু প্রতীক দিয়ে সরিয়ে ফেলা । এ যেন মানববোমা । উদ্দিষ্ট প্রতীকটাকে ধ্বংস করে দিয়ে নিজেও মরে যাবে । এমন জ্ঞানের ব্যবহার, যা পুরোনো জ্ঞানকে মেরে ফেলবে অথচ নতুন 'জ্ঞানের বোঝা' হয়ে দেখা দেবে না ।
পঞ্চম পর্ব : যড়যন্ত্র : উচ্চাটন
( অ্যান্টি এস্টাবলিশমেন্ট রিভোল্ট প্রোগ্রামিং : অ্যান আইটি এক্সপ্লোর )
সবাই জানেন কমপিউটারের দুনিয়ায় উইনডোর নানা ভারশন প্রকাশিত হয়েছে । উইনডো ৯৫, উইনডো ০৭, উইনডো ৯৮ ভারসন ১, উইনডো ৯৮ ভারসন ২, উইনডো মিলেনিয়াম ভারসন ইত্যাদি ইত্যাদি । তবে যেটা অনেকেই নজর করেননি, তা হল প্রতিষ্ঠান বিরোধিতারও অনেকগুলি ভারসন আমাদের মার্কেটে চালু আছে । প্রতিটি ভারসনের আবার অনেকগুলি করে এডিশন রয়েছে । যার যেটা পছন্দ তিনি সেটা কেনেন, ব্যবহার করেন । ক্রেতার অবগতির জন্য এখানে কয়েকটি ভারসনের একটি করে এডিশন-এর অতি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হল ।
ষষ্ঠ পর্ব : প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা : ভারসন ১
( লঞ্চড বাই শিবশম্ভু পাষণ্ড/সনাতন এডিশন )
ইট ইজ আ প্রিমিটিভ এডিশন অ্যান্ড প্রেজেন্টলি নট অ্যাভেলেবল ইন দ্য মার্কেট।
সপ্তম পর্ব : প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা : ২
( লঞ্চড বাই বাল্মীকি/চণ্ডাশোক এডিশন )
১) শাসক...ব্রাহ্মণ
২) শাসিত...ক্ষত্রিয় বৈশ্য শুদ্র ও অন্যান্য ম্লেচ্ছ সম্প্রদায়
৩) বিরোধের কারণ...সামাজিক মুক্তধারার উপরে নির্মিত বাঁধ
৪) বাঁধের কারিগর...কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস ও তাঁর শিষ্যগণ
৫) বাঁধ গড়ার উপাদান...সামাজিক প্রতীকের পাথরপ্রতিমা দিয়ে দিয়ে
৬) বাঁধ ভাঙার মন্ত্র...পালটা প্রতীকের পাথর দিয়ে দিয়ে
৭) সুয়ো-রাজকুমার...রাবণ অ্যাসোশিয়েটস
৮) দুয়ো-রাজকুমার...রাজকুমার সিদ্ধার্থ গৌতম
৯) ছদ্ম দুয়ো-রাজকুমার...বিভীষণ
১০) বিদ্রোহের নেতা...দাশরথীগণ
১১) ছদ্ম বিদ্রোহী নেতা...ঃঃঃঃঃঃঃঃ
১২) বিদ্রোহের ( স্লো ) গান...রাম নাম সত্য হ্যায়
১৩ ) আধপাগলা...জটায়ু
১৪ ) গাধা...হনুমান
অষ্টম পর্ব : প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা : ভারসন ৩
( লঞ্চড বাই কে.ডি.বেদব্যাস/রিঅ্যাকটিভ এডিশন )
১) শাসক...দেবগণ
২) শাসিত...অসুরগণ
৩) বিরোধের কারণ...সামাজিক মুক্তধারার উপরে নির্মিত বাঁধ
৪) বাঁধের কারিগর...বিশ্বকর্মা
৫) বাঁধ গড়ার উপাদান...সামাজিক প্রতীকের পাথর দিয়ে দিয়ে
৬) বাঁধ ভাঙার মন্ত্র...পালটা প্রতীকের পাথর দিয়ে দিয়ে
৭) সুয়ো-রাজকুমার...গন্ধর্বগণ
৮) দুয়ো-রাজকুমার...শঙ্করাচার্য
৯) ছদ্ম দুয়ো-রাজকুমার...কুমারিল ভট্ট
১০ ) বিদ্রোহের নেতা...জরৎকারুপুত্র আস্তীক
১১) ছদ্ম বিদ্রোহী নেতা...ঃঃঃঃঃঃঃঃ
১২ ) বিদ্রোহের ( স্লো ) গান...চাতুর্ব্বর্ণ্যব্যবস্হানং যস্মিন দেশে প্রবর্ততে । আর্যদেশঃ স বিজ্ঞেয়
১৩ ) আধপাগলা...লোমশ মুনি
১৪ ) গাধা...যাদবগণ
নবম পর্ব : প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা : ভারসন ৪
( লঞ্চড বাই কার্ল মার্কস/প্যারি কমিউন এডিশন )
১) শাসক...সহস্রমুখ বুর্জোয়া
২) শাসিত...সর্বহারা শ্রমিক কৃষক পেটিবুর্জোয়া শ্রেণি
৩) বিরোধের কারণ...কেবলমাত্র রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তধারার উপরে নির্মিত বাঁধগুলি
৪) বাঁধের কারিগর...যন্ত্ররাজ বিভূতি ও ভৈরবমন্ত্রে দীক্ষিত সন্ন্যাসীর দল
৫) বাঁধ গড়ার উপাদান...রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতীকের পাথর দিয়ে দিয়ে
৬) বাঁধ ভাঙার মন্ত্র...বন্দুকের নল । পালটা প্রতীকের পাথর দিয়ে দিয়ে
৭) সুয়ো-রাজকুমার...সাম্রাজ্যবাদী নবীন বুর্জোয়া/প্রতিবিপ্লবী
৮) দুয়ো-রাজকুমার...ডিক্লাসড ( অবক্ষিপ্ত ) বুদ্ধিজীবী
৯) ছদ্ম দুয়ো-রাজকুমার...পাতিবুর্জোয়া
১০ ) বিদ্রোহের নেতা...কমিউনিস্ট বিপ্লবী
১১) ছদ্ম বিদ্রোহী নেতা...অতিবিপ্লবী
১২) বিদ্রোহের ( স্লো ) গান...ইনকিলাব জিন্দাবাদ/জাগো জাগো জাগো সর্বহারা
১৩) আধপাগলা...কমিউনিস্ট সাহিত্য ও সংস্কৃতি কর্মী
১৪ ) গাধা...একনিষ্ঠ কমিউনিস্ট কর্মী ( শ্রমিক কৃষক )
দশম পর্ব : প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা : ভারসন ৫
( লঞ্চড বাই রবীন্দ্রনাথ ট্যাগোর/সেকেন্ড ওয়র্ল্ড ওয়ার এডিশন । )
১) শাসক...রাজা রণজিৎ
২) শাসিত...উত্তরকূট ও শিবতরাইয়ের প্রজাবৃন্দ
৩) বিরোধের কারণ...মুক্তধারার উপর নির্মিত বাঁধ
৪) বাঁধের কারিগর...যন্ত্ররাজ বিভূতি ও ভৈরবমন্ত্রে দীক্ষিত সন্ন্যাসীর দল
৫) বাঁধ গড়ার উপাদান...ঃঃঃঃঃঃঃঃ
৬) বাঁধ ভাঙার মন্ত্র...ছিদ্রস্হানে আঘাত
৭) সুয়ো-রাজকুমার...ঃঃঃঃঃঃঃঃ
৮) দুয়ো-রাজকুমার...'স্বজনবিদ্রোহী' খুড়ো বিশ্বজিৎ ও যুবরাজ অভিজিৎ
৯) ছদ্ম দুয়ো-রাজকুমার...ঃঃঃঃঃঃঃঃ
১০) বিদ্রোহের নেতা...ধনঞ্জয় বৈরাগী
১১) ছদ্ম বিদ্রোহী নেতা...ঃঃঃঃঃঃঃঃ
১২) বিদ্রোহের ( স্লো ) গান...বাঁধ ভেঙে দাও বাঁধ ভেঙে দাও দাআআআআও
১৩) আধপাগলা...গণেশ
১৪ ) গাধা...সঞ্জয়
একাদশতম পর্ব : প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা : ভারসন ৬
( লঞ্চড বাই পবং এক্সক্লুসিভস / লেটেস্ট এডিশন )
১) শাসক...প্রগতিশীল ( মার্কসবাদী, কমিউনিস্ট, বিপ্লবী)
২) শাসিত...জনগণ
৩) বিরোধের কারণ...সর্বহারার মুখে নির্মিত বাঁধসমূহ
৪) বাঁধের কারিগর...প্রত্যেক ধারার নিজ-নিজ যন্ত্ররাজ বিভূতি ও তত্তদ সন্ন্যাসীর দল
৫) বাঁধ গড়ার উপাদান...তত্তদ ধারার নিজস্ব প্রতীকের পাথর দিয়ে দিয়ে
৬) বাঁধ ভাঙার মন্ত্র...ছিদ্রস্হানে আঘাত । সেই ধারার পালটা প্রতীক দিয়ে প্রতীকবদল ।
৭ ) সুয়ো-রাজকুমার...বাবুবংশের উত্তরাধিকারীগণ, বাবুভায়াগণ
৮) দুয়ো-রাজকুমার...হাংরি, শাস্ত্রবিরোধী, নকশাল, বিচ্ছিন্নতাবাদী, পোস্টমডার্ন ইত্যাদি
৯) ছদ্ম দুয়ো-রাজকুমার...মার্কসবাদী কমিউনিস্ট বিপ্লবী
১০) বিদ্রোহের নেতা...মার্কসবাদী কমিউনিস্ট বিপ্লবী
১১) ছদ্ম বিদ্রোহী নেতা...মার্কসবাদী কমিউনিস্ট বিপ্লবী, অতিবিপ্লবী, উগ্রপন্হী
১২) বিদ্রোহের ( স্লো ) গান...কে চেল্লায় শালা, কে চেল্লায় এই ভোরবেলা
১৩ ) আধপাগলা...শম্ভু রক্ষিত অ্যান্ড অ্যাসিসিয়েটস
১৪ ) গাধা...সেকেন্ড লাইন হাংরি, শাস্ত্রবিরোধী ও নকশাল এবং ফোর্থ লাইন মার্কসবাদী
দ্বাদশতম পর্ব : 'প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা : মিলেনিয়াম ভারসন'
( দিস প্রডাক্ট ইজ নাউ অ্যাবানডন্ড । অ্যাকর্ডিং টু কমপিউটার ইনজিনিয়ার্স, দ্য এসট্যাবলিশমেন্ট রিভোল্ট প্রোগ্রামিং ইজ বিকামিং অবসলিট ইন দ্য প্রেজেন্ট কনটেক্সট । )
বলে রাখা ভালো, এই অ্যান্টি-এসট্যাবলিশমেন্ট রিভোল্ট প্রোগ্রামিং স্বভাবতই ভালনারেবল । কোনো অ্যান্টি-ভাইরাস ব্যবস্হাই একে বাঁচানোর ক্ষেত্রে সফল হতে পারেনি । অর্থাৎ এই প্রোগ্রাম আদৌ ভাইরাসপ্রুফ নয় । যখন তখন ক্র্যাশ করে যায় । এই প্রোগ্রামিং যে আজকাল আর তেমন বিকোচ্ছে না, সেটাই তার অন্যতম কারণ ।
আরও কারণ আছে । আজকের মানবসমাজ একাকারের যুগে পা রেখে ফেলেছে । ফলে, শাসক-শাসিতের অ্যান্টাগনিজম ক্রমশ কমপ্লিমেন্টারির দিকে টাল খেয়ে যাচ্ছে । গোটা ব্যবস্হাটা, তার সমগ্র প্রেক্ষাপট ,সবই 'এফেক্টিভ ফ্যাক্টর' রূপে সক্রিয় হয়ে উঠেছে । মানবসমাজ, জীবজগৎ ও জড়জগৎকে নিয়ে যে-সমগ্রব্যবস্হা, সেটি ঠিক থাকছে কি না, মানব সভ্যতার অস্তিত্বের পক্ষে অনুকূল থাকছে কি না, সেসব কথাও আজ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে । অথচ প্রচলিত ধনতান্ত্রিক বা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্হাগুলি এই পরিস্হিতির তুলনায় সেকেলে হয়ে গেছে বা যাচ্ছে । বিজ্ঞানী মারি গেলম্যান-এর মতে, ...neither greedy capitalists nor dogmatic communists have sufficient respect for the larger system of which we are merely a part. স্বভাবতই প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার প্রোগ্রামিংগুলিও আজকের প্রেক্ষিতে সেকেলে হয়ে গেছে । সন্মুখস্হ পরিস্হিতির বিচার বিবেচনা করে আজকের দিনের পোস্টমডার্ন চিন্তাবিদরা এমন অদ্বৈত প্রোগ্রামিং-এর কথা ভাবতে শুরু করেছেন, যা বদ্ধধারাগুলিকে কেবল মুক্তধারাতেই পরিণত করবে না ; সমগ্র ব্যবস্হাটিকেও আরও সুসংহত করবে । আর, সেটা করতে গিয়ে তাঁরা বিগত যুগের প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার প্রোগ্রামিংসমূহের সমস্ত অর্জনগুলিরও সারসংগ্রহ করে নিচ্ছেন ।
সংগৃহীত ও সারে কী রয়েছে ? শাসক-শাসিতের ( পুরুষ-প্রকৃতির, কনটেন্ট-ফর্মের ) দ্বৈতাদ্বৈত অস্তিত্বের পরিবর্তনের মূল যে-কারিকা, তার সরবরাহ ঘটে শাসিতের তরফ থেকে নয় ; শাসকের তরফ থেকেই । শাসিত তো শাসকের বিরোধী হয়ে থাকেই । কিন্তু তাতে কিছু হয় না । যে গোপন কথাগুলির ওপর ক্ষমতা টিকে থাকে, তার সব কথা শাসিতেরা কখনও জানতে পারে না বলেই শাসন সম্ভব হয় । জানতে পারে তারাই যারা ওই প্রাসাদের অংশ, উত্তরাধিকারী । সেই কারণে দলছুট প্রাসাদত্যাগী দুয়ো-রাজকুমারেরা বিদ্রোহীর দলে যোগ না দিলে কোনও রাজপ্রাসাদেরই পতন সম্ভব নয় ; এটাই ছিল এতদিনের অঙ্ক। তাই শাসনের সমস্ত খেলাই এতদিন ছিল ওই বিদ্রোহী রাজকুমারের আসনটিকে ঘিরে । কারণ তার ভূমিকার ওপরই নির্ভর করত ব্যবস্হাটি বদলাবে কি না । সেই কারণে দুয়ো-রাজকুমারের তপস্যা ভেস্তে দেওয়ার খেলা, তার ভূমিকাকে নানাভাবে বিগড়ে দেয়ার খেলাই ক্ষমতার অন্যতম খেলা ছিল । সেই কারণে, বিদ্রোহী নেতা ও দুয়ো-রাজকুমারকে আগেভাগে গুমখুন করে তার আসনটি শাসকই ছদ্মবেশীদের বসিয়ে দখল করে রেখে দিত । কিন্তু সম্প্রতি ট্রান্সপারেন্সির ডাক দিয়ে বিশ্বের সমস্ত দুয়ো-রাজকুমারেরা ক্ষমতার সেই সব খেলাই ভেস্তে দিয়েছে, দিচ্ছে । এখন কেবল ডিসক্লোজ করে যাও । কেবল মেলে ধরা, যাতে সবাই সবকিছি দেখতে পায় । এতে শাসক-শাসিতের পরিচালক-পরিচালিতে উন্নীত না হয়ে কোনও উপায়ই থাকে না । শাসন অবসানের এযুগের এই পথ ।
ত্রয়োদশতম পর্ব : 'ষড়যন্ত্র : বশীকরণ'
( শেষ দুয়ো-রাজকুমারের কলাপ : এক ডক্টরেরটকামী ছাত্রের থিসিস থেকে )
বাংলার সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দুয়ো-রাজকুমার ঠিক কী কী করেছিলেন, তা জানার জন্য আমি তাঁর বিষয়ে অনুসন্ধান চালাই । এক সময় জানতে পারি, তিনি যাদের সঙ্গে থাকতেন, সেই আধপাগলা মানুষগুলি তাঁর সম্পর্কে অনেক কিছু জানেন । তাঁর অনেক নথিপত্রও নাকি তাঁদের কাছে রয়েছে । একথা জানতে পারার পর, আমি সেই আধপাগলা মানুষগুলির খোঁজখবর করি এবং অনেক তেল পুড়িয়ে অবশেষে তাদের দু;জনকে খুঁজে বার করতে সক্ষম হই । তাঁদের সঙ্গে আমার যে কথোপকথন হয়েছিল, তা নিম্নে বর্ণিত হল :
আমি : শুনেছি, আপনাদের সঙ্গে দুয়ো-রাজকুমারের ক্লোজ রিলেশান ছিল?
আধপাগলা ১ : ক্লোজ রিলেশান কোথায় দেখলে ? ও তো ডিসক্লোজ রিলেশান । যতো পারো ডিসক্লোজ করে দাও । কোনও আবরণ যেন না থাকে । আবরণেই তো বাধা । আটকা আটকি । ঢেকে চেপে রাখা । অন্ধকার করে রাখা । অন্ধ করে রাখা । অন্ধকারে কী হয় জানো ? জানো না ? শ্বাপদেরা বাসা বাঁধে ।
আমি : বলছিলুম কী, দুয়ো-রাজকুমারের সাথে আপনাদের আলাপ হল কেমন করে ?
আধপাগলা ২ : সে অনেক কথা । পেথম সে এসেচিল ভোলানাথ সেজে । আমার ঠাকুদ্দার বাবার বাবাদেরও আগে, অনেকেই তাকে দেখেছিল ।
আমি : তার কথা আমি জানতে চাইছি না । যার সঙ্গে মুক্তির দশক এবং তারপরেও আপনাদের দেখা হয়েছিল, তার কথা বলুন । তার সাথে আপনাদের আলাপ হল কেমন করে, ঘনিষ্ঠতা হল কেমন করে ?
আধপাগলা ২ : ঘনিষ্ঠতা আর হল কই ? ঘন হবার আগেই তো ইষ্টদেবতা বাধ সাধলেন । গাধা এলো, গাধার টুপি এলো, চুনকালি মাখানো হল, তারপর সব হাহা হিহি হয়ে গেল । তাতে ইষ্ট ছিল না অনিষ্ট ছিল সে তো আর ঠাহর করা গেল না ।
আধপাগলা ১ : যতদূর জানি, ও এসেছিল অঙ্গদেশের পাটলিপুত্র থেকে । শুনেছি বাবুকালচারের যে দুয়োরানি বাংলার বাইরে প্রত্যন্ত শহরগুলিতে আশ্রয় নিয়েছিল, ও তাদেরই এক সন্তান । সাবর্ণ চৌধুরী নামে কলকাতার যে-বিখ্যাত বাবু রাজবংশের প্রতিষ্ঠা, ও সেই বাবুকালচারের একজন অবহেলিত অবক্ষিপ্ত উত্তরাধিকারী, এক দুয়ো-রাজকুমার ।
আমি : শুনেছি, ওই দুয়ো-রাজকুমার যাচ্ছেতাই গালাগালি করত, অশ্লীল ভাষায় কথা বলত, অশালীন গান গাইত, গাঁজা ভাঙ খেতো, নোংরা জীবন যাপন করত -- এসব ক সত্যি ?
আধপাগলা ১ : আমরা তো সবাই বস্তিতে থাকি, থাকি গণ্ডগাঁয়ে, আর ও তো আমদের সাথেই থাকত । আমাদের জীবন যাপন যেরকম, সেরকমই থাকত । সেটা অশ্লীল কি অশ্লীল নয়, সে আপনারাই জানেন । আর গালাগালির কথা যদি বলেন, সে তো আপনি থাকলেও করতেন । নিজের ভাই হয়ে সুয়ো-রাজকুমাররা ওর সাথে কোন মন্দ ব্যবহারটা করতে বাকি রেখেছিল শুনি ? ও যে ডেলি দু'চারটা খুনখারাবি করেনি, কেবল শালা-বাঞ্চোৎ করেছে, সেটাই তো অনেক ভদ্র ব্যবহার ।
আমি : শুনেছি, সেপাইরা ওকে যখন জেলখানায় নিয়ে যায়, তখন এক-দু'জন সুয়ো-রাজকুমারই ওর হয়ে সত্যিমিথ্যে সাক্ষ্য দিয়েছিল, বলেছিল. 'কই, ও তো রাজার মাকে ডাইনি বলেনি, যে ওটাকে ছেড়ে দে ।' কথাটা কি ঠিক ?
আধপাগলা ২ : আরে সেটাই তো কাল হল । যে এক-দু'জন দুয়ো রাজকুমার 'কনখল' কমপ্লেক্সে ফ্ল্যাট কিনে সুয়ো-রাজকুমারের দলে ভিড়ে গিয়েছিল, তারাই ওরকম সাক্ষ্য দয়েছিল । তাই, ওর মনের এক কোণায় একটা বিশ্বাস থেকে গেল যে, সকল সুয়ো-রাজকুমার সমান শয়তান নয়, এক-দু'জন ভালো হয় । কিন্তু 'কনখল'-এর বাসিন্দা মাত্রেই যে 'সচ্ছল' ( সচ-ছল বা সৎ সেজে ছলনাকারী ) হয়, সেটা সে খেয়াল করেনি । অনেকে বলে, ওই বিশ্বাসের জন্যেই ও নাকি হেরে গেল ।
আমি : সাংস্কৃতিক-বাঁধ ভাঙার কলাকৌশল সে নাকি খুব ভালোভাবেই জানত, আর সে-রহস্য আপনাদেরকে সে নাকি বলে গিয়েছে । কথাটা কি সত্যি ?
আধপাগলা ২ : আমাকে ওসব বলেনি বাবা । আমি সেসব কতা শুনিনি । বিশ্বাস করো ভাই, ওসব কতা আমি এক্কেরে শুনিনিকো । রাজার দেয়া বাঁধ বলে কতা । ভাঙব বললেই হল । সেপাই আচে না, সান্ত্রী আচে না ।
আধপাগলা ১ : দেখো বাছা । প্রত্যেক বাঁধের একটা না একটা ছিদ্র থাকে । সেটা সে জেনেছিল । সেখানে যন্ত্রাসুরকে আঘাত করলেই বাঁধটা ভেঙে পড়ে । কিন্তু কোন বাঁধের কোথায় ত্রুটি সেসব কথা আমার জানা নেই । যে দুয়ো-রাজকুমারের সাথে আমার দেখা হয়েছিল, সে কেবল সাহিত্য-সংস্কৃতির বাঁধের রহস্যগুলো বলত । তার সব কথা ভালো বোঝাও যেত না । তার দেওয়া একটা কাগজ আছে আমার কাছে, সেটায় সেসব সে লিখেও দিয়েছিল । তার কোনো কথাই আমার মাথায় ঢোকেনি । দেখো, তুমি বুঝতে পারো কি না ।
শেষ পর্ব : ম্লেচ্ছিতবিকল্প
সাহিত্য সংস্কৃতির সাবলীল ধারার সামনে ওরা বাঁধ বেঁধেছে অজস্র প্রতীকের পাথর দিয়ে । সেগুলিকে সাময়িক প্রত্যয়ের পাথরপ্রতিমা দিয়ে রিপ্লেস করে ফেলা দরকার । বাঁধটা যেহেতু বিশাল, অজস্র পাথর গেঁথে গেঁথে তৈরি, তাই এই ভেঙে ফেলার কাজটাও বিশাল । এটা সফল করবার জন্য আরও অনেকের হাত লাগানো দরকার । আমি আমার সধ্যমতো এই রিপ্লেসমেন্টের কাজগুলো করার চেষ্টা করে থাকি এইভাবে :-
১) শিল্পের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা ( একালের ) কবিতা রচনার প্রধান শর্ত ।
২) আমার রচনা বাংলা ভাষার একটি বিশেষ কাঠামোকে সর্বজনীন করে তোলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ । প্রতিবাদ সংস্কৃতি পিটিয়ে কলকেতিয়া করে তোলার বিরুদ্ধে ।
৩) পশ্চিমবঙ্গে বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপকরা ঐতিহ্যের যে মানদণ্ড গড়ে ফেলেছেন তাকে অস্বীকার করাটা যেন তাঁদেরই অপমান করার উদ্দেশ্যে, এমন একটা ধুয়ো আজ সর্বজনস্বীকৃত । তাই শিল্প বানাবার বাঙালি চেতনা থেকে কবিতাকে মুক্ত করার চেষ্টাকে ভালো চোখে দেখা হয় না । ওদিকে কবিতা থেকে সিমবলিস্ট এবং সুররিয়ালিস্ট চাপ বাদ দেবার আইডিয়া আমার মাথায় ঘুরঘুর করছিল ।
৪) আমি মনে করি, কবিতায় ভাষার খেলা, ইমেজ গেম, রিদম গেম, মেটাফিজিক্স গেম অবশ্য বর্জনীয়, কেননা ওগুলির সাহায্যে মানুষের অসহায়তা নিয়ে জোচ্চুরি করা হয় ।
৫) আমি তো সিমবলিস্ট কবি নই যে একটা চিত্রকল্পকে কোনো কিছুর পপতীক হিসেবে সংজ্ঞায়িত করব । ( বিষয়, আঙ্গিক, উপমা, ছন্দ, প্রতীক, রূপক, অলঙ্কার -- সর্বত্রই অ্যাটাক ) ।
৬) একদিকে চিৎকার, বিপরীতে ফিসফিসানি -- এই দিয়ে আমি কবিতার আধুনিক স্বরকে ভেঙে দিই ।
৭) প্রেম ও অপ্রেম, শরীর ও মন ইত্যাদি যুগ্মবৈপরীত্য যেভাবে বাংলা কবিতায় তোয়াজ করা হয়েছে এতাবৎ এবং তার অন্তর্গত সন্ত্রাসটিকে কবিরা এতকাল যে-চেতনা প্রয়োগে বানচাল করেছেন, আমি তা সম্পূর্ণ অস্বীকার করে প্রেমকে সেনসরহীন স্বরূপে উপস্হাপন করি । প্রেম বা কবিতা এখন বিনোদন নয় ।
৮ ) আমি ষাটের দশকের শুরু থেকেই অলঙ্কার বর্জনের কথা বলে আসছি । অধুনান্তিক চেতনাটি নিরাভরণ । আমার কবিতায় কবিত্বের সন্ত্রাসকে উৎসাহিত প্ররোচিত করার প্রয়াস যাথার্থ দিতে চায় অলঙ্কারহীনতাকে । আমার কবিতা দার্শনিক স্তরে, সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক-আর্থিক-নৈতিক স্হিতাবস্হার বিরুদ্ধে একটি স্ব-স্বীকৃত দ্রোহতর্ক ।
৯ ) আমি সত্যিই শিল্পের বিরুদ্ধে ও সংস্কৃতির স্বপক্ষে বলতে চেয়েছিলুম । পরাবাস্তববাদের আদলে শিল্পবিরোধিতার পালটা শিল্পের কথা বলিনি ।
১০) সমস্ত কবিতার ক্ষেত্রে এক নিয়ম হতে পারে না । কনটেক্সট অনুসারে প্রত্যেকটির বয়নই তার মতো ।এমন কবিতাও অতএব হতে পারে, যেখানে 'আলো' প্রতিনিধিত্ব করে না কান্টিয় বা বৈদিক আলোর । কেননা এমন পরিস্হিতি তো দেখাই যাচ্ছে যেখানে 'আলো' নামক লোগোটি ঘৃণ্য হয়ে গেছে । রেললাইনে হাত-পা বাঁধা যে পড়ে আছে, তার কাছে আগন্তুক আলো কী ? কিংবা যে আগুনের পরশমণি থানার সেপাইদের জ্বলন্ত সিগারেট হয়ে কয়েদি চাষির লিঙ্গে ছ্যাঁকা হয়ে লাগে, তাকে কী বলা হবে ? এসব ক্ষেত্রে প্রথাবাহিত সাংস্কৃতিক অনুমানগুলিকে আমার কবিতা নস্যাৎ করতে চায় । কবির কন্ঠস্বর নামক বদল্যারীয় জীবনানন্দীয় তর্কটি এর দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয় এবং উত্তরাধিকারমুক্ত করা হয় কবিত্বকে ।
১১ ) গতানুগতিক কবিতার অনুশাসনকে ছন্দের তেল চটচটে আঙ্গিকেই ভেঙে ফেলতে চাই বলে আমি কখনও কখনও ভাষার অনচ্ছ বৈশিষ্ট্যকে ব্যবহার করে থাকি, যাতে এমন একটা আদল পাওয়া যায়, যা বর্তমান অসম্বদ্ধতাকে অসংলগ্নতাকে আকস্মিকতার সন্নিবেশকে স্বতঃস্ফূর্ত করতে পারে । সেক্ষেত্রে তাই আমার কবিতার পাঠকৃতিটি ইচ্ছাকৃতভাবে ছেতরানো, ছেঁড়াখোঁড়া, তাপ্পিমারা, বহুরঙা ও আসক্তিবিরোধী ।
১২ ) ইংরেজরা বিদেয় হবার পর এবং দিল্লির দরবারে অজস্র জোকারের আবির্ভাবের ঘনঘটায় যে-ইতিহাসোত্তর কালখণ্ডটির হামলায় শব্দজগৎ ও ভাষাপৃথিবী আক্রান্ত, কবিতার ওই প্রোটোকলবর্জিত প্রতীকবাদবিরোধী এলাকাটির দখল নেয়া জরুরি ।
১৩ ) 'সত্য' যে সর্বজনীন নাও হতে পারে, সে কথাটা বলা দরকার বলেই বলি ।
১৪ ) আমি মনে করেছিলুম যে, একজন কবি হিসেবে মন ও দেহের যুগ্মবৈপরীত্যের তত্বটিকে চ্যালেঞ্জ জানানো দরকার আর সেটাই আমি করেছি, যেখানে পেরেছি ।
১৫ ) বাস্তবের তৈরি অবাস্তবতায়, স্হিরতার গড়া অস্হিরতায়, মুহূর্ত দিয়ে গড়া কালপ্রবাহে, অগতি থেকে উৎসারিত গতিতে, অবজেক্ট/সাবজেক্ট বিভাজনটি ভেঙে পড়ে ।
১৬ ) দাঙ্গাকে প্রান্তিকের ওপর চাপিয়ে দেয় কেন্দ্র অথচ তা মসনদের চাকুমালিকদের অন্দরমহলের গল্প । তারা যেহেতু ক্ষমতার কেন্দ্রে, সত্যের নিয়ন্তা তারাই । শাসক মাত্রেই আধিপত্যবাদী, তা সে যে-তত্বেরই মালিক হোক ।
১৭ ) কবিতায় ঝোড়ো হাওয়া আর পোড়ো বাড়ির ভাঙা দরজার মেলবন্ধন তখনই সম্ভব যখন বাস্তবে আধিপত্যবাদী শর্তগুলো মেনে নেওয়া হচ্ছে । আমার রচনার গেম-প্ল্যান মূলত সেই আদি সাংস্কৃতিক ভঙ্গুরতা থেকে উপজাত । হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অবিদ্যমান যুদ্ধ'-এর মতো যা অবর্তমান সেইটেই আমার রচনায় উপস্হিত হয়ে দশ পঙক্তির খেলা করে । খেলাটি সমাপ্ত হিসাবে ঘোষিত হবে তখনই, যখন ধাঁধাটির সমাধান হবে। নয়তো চলতে থাকবে মর্মার্থ-সঙ্কটাপন্ন শব্দাবলীর ঝোড়ো হাওয়া । মাত্রাতিরিক্ত মিলের মাত্রাতিরিক্ত নাটুকেপনা চলতে থাকবে ।
১৮ ) ছবিগুলি ভাষার সাংস্কৃতিক নির্দেশের অন্তর্গত এবং তা দাঙ্গার সন্ত্রাসের বাইরেকার 'আমির' আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠিত করে । দাঙ্গার সন্ত্রাস স্ট্রাকচার্ড হয় । রাজপথে পড়ে থাকা সন্ত্রাস-পরবর্তী টুকিটাকি প্রকৃতপক্ষে অবাস্তব ঘটনাবলীর সত্য ।
১৯ ) প্রত্যন্তকে, আধুনিকতা যে নান্দনিক সন্ত্রাসে নিয়ে গিয়ে আছড়েছে, স্বগতোক্তি ছাড়া সমস্ত শব্দ এবং ধ্বনি সেই চত্বরে অর্থহীন । সন্ত্রাসের উপাদান এক্ষেত্রে স্তব্ধতা, শিশির, ঝিঁঝি, নক্ষত্র, শীত, পাথর ইত্যাদি যা সনাতনি কবিতায় তথাকথিত সৌন্দর্য বানাবার কাজে লাগে । মাত্রা গুনে-গুনে যে ধরণের ডিজিটাল কবিতা বাজারচালু, সেই ডিজিটাল যান্ত্রিক কবিত্ব ভাঙা হয়েছে । ছন্দের ভেতরে ভেতরে কোনও মানে ঢোকানো নেই, যা কিছু মানে তা উপরিতলেই ভাসছে ।
২০ ) ছয়ের দশকেও বাংলা কবিতায় থাকত চিত্র, চিত্রকল্প । আমি ব্যবহার করি উপচিত্র । রূপক নয়, লক্ষণগুলোই আমার হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ।
২১ ) লিরিকের জমিতে রোমান্টিক চেতনার চাষ ভালো হয়, কেননা লেখকের কোনো নৈতিক দায় থাকে না । আমি কবিতায় ভঙ্গুরতা আগাগোড়া বজায় রাখি কাঠামোটিকে 'অ্যান্টিলিরিক' করে তোলার জন্য । একদিকে লিরিকের অচলাবস্হা থেকে এবং অপরদিকে ক্ষমতার তাত্বিক খবরদারি থেকে দূরে থাকা দরকার । লেখাকে তাই কাউন্টার-হিগেমনিক করে তোলা দরকার ।
২২ ) প্রতিষ্ঠিত ফর্ম মাত্রেই প্রতিষ্ঠানের কুক্ষিগত, তাই তাকে ভাঙা জরুরি । জরুরি প্রতিষ্ঠিত জনপ্রিয় মনোভাবের অবিনির্মাণ । পাঠকৃতি যেন স্বেচ্ছায় আত্মদীর্ণ, অসমতল, দ্বন্দ্ব-আবিল, অক্ষহীন, দলছুট, আপত্তিসূচক, উভমুখী, অসংহত, ঘরাণা-বহির্ভূত এবং চোরা-আক্রমণাত্মক হয়ে যায় । কারণ কবি মানেই তো 'চোরাযোদ্ধা' ।
২৩ ) অত্যন্ত বেশি ব্যাকরণবোধ থেকে সাজানো-গোছানো সমাজের ধান্দার দরুন পয়দা হয় ওদের স্তালিন ও আমদের সঞ্জয় গান্ধির আদর্শ । শুভর কুহকে আত্মসমর্পণ করে নাৎসিরা অশুভর রাজপথ উদ্বোধন করেছিল । সবাইকে পিটিয়ে সমান করার ব্যাষ্টিবাদের শুভত্ব মূলত একটি মৌলবাদী জবরদস্তি যা গদ্য কবিতাকেও ঢোকাতে চায় ছন্দের তালিবানি জেলখানাণ এবং আধমাত্রা সিকিমাত্রার বেয়াদপিকে শায়েস্তা করতে চায় অ্যাকাডেমিক গেস্টাপোদের নাকচের অস্ত্র দ্বারা । আমার রচনা তা মানে না এবং না-মানার ঝুঁকি নেয় ।
২৪ ) কবিতায় আমি আপইয়েলিং ঢোকাই । আপওয়েলিং কোনো নির্মাণ নয়, সৃজনশীলতা নয়, পুনরাবৃত্তি নয়, ভাষাবয়ন নয় । ফ্রেম থেকে যাতে উপচিত্রগুলো বেরিয়ে যায়, তাই তাদের মধ্যে কোনও বার্তা পুরে দিই না । তারা অঙ্গপ্রত্যঙ্গহীন । যা চোখের সামনে তুলে ধরা যায় না, তাকেই তুলে ধরা । বিজ্ঞানীরা যেমন বলেন, যা চোখে দেখা যায় তার অস্তিত্ব নির্ভর করে, যা চোখে দেখা যায় তার ওপর। যেটা উপস্হিত ।
 উদয়ন ঘোষ | 122.179.172.247 | ২৪ আগস্ট ২০২১ ১৯:৩০734902
উদয়ন ঘোষ | 122.179.172.247 | ২৪ আগস্ট ২০২১ ১৯:৩০734902উদয়ন ঘোষ : মলয় পোস্টকলোনিয়াল, মলয় পোস্টমডার্ন
যত দিন যাচ্ছে, মলয়ের লেখা যত পড়ছি, ততই মনে হচ্ছে, তাঁকে নিয়ে মহাভারত লেখা যায় । মহাভারত অবশ্য কথার কথা, আসলে মলয় সম্পর্কে বহুবিধ কথা লেখা যায় । সেজন্য নিজের সুবিধার্থে এবং টাইম অ্যাণ্ড স্পেস ভেবে, আমি স্হির করেছি, মলয় রায়চৌধুরী সম্পর্কে মাত্র ওই কথা লিখি, অর্থাৎ মলয়ের পোস্টকলোনিয়ালিজম এবং তাঁর পোস্টমডার্নিজম ।
আর যে যাই ভাবুক, আমি ভাবি, এদেশে পোস্টকলোনিয়াল না হলে পোস্টমডার্ন হওয়া যায় না ।
আদিতেই বলে রাখা ভালো, ওই পোস্টকলোনিয়ালিজম ও পোস্টমডার্নিজম সম্পর্কে আমার ধারণাকে, আমি, কিছুকাল হল, নিজের কাছে অন্তত, স্বচ্ছ করে রাখতে পেরেছি । কেননা দুটোই ঐতিহাসিক ভাববস্তুগত নির্দিষ্ট এক অবজেকটিভ কোরিলেশানে আছে । এবং দুটোই এককভাবে কোনও দর্শন, অথবা আচরণ কিংবা ঢঙ অথবা প্রবণতা নয়, তদুপরি এককভাবে এই দুই কোনও সাংস্কৃতিক অথবা পরিকাঠামোগত স্ফূরণও নয় । এবং এই দুই ওই সবকিছুর যোগফলও নয় । অথভ ওই পোস্টকলোনিয়ালিজম ও পোস্টমডার্নিজমে ওই সব তথাকথিত কোনও নির্দিষ্ট দর্শন, আচরণ, ঢঙ, প্রবণতা, সাংস্কৃতিক/পারকাঠামোগত স্ফূরণ ইত্যাদি ইতস্তত থাকলেও থাকতে পারে । কিছু গবেষক, ক্রিটিক, উৎসাহী পাঠক, অথবা ওই দুই ইজমের ধ্বজাধারী সেবক, লেখক, কিংবা সদাসর্বদা যাঁরা যে-কোনও ইজমের হঠাৎ দার্শনিক বনে যান, অথবা তদনুরূপ সমাজবিজ্ঞানী ওই দুই ইজমে, ওপরে, যা যা লক্ষণের কথা আছে -- তার সবগুলি, অথবা একাধিক, কিংবা যে-কোনও একটি লক্ষণকে ওই দুই ইজমের ধ্রুবতারা মনে করতে পারেন ।
আমি বরাবরই ওই সব ইজম, এবং তৎসংক্রান্ত নানাবিধ টাইটেল-সাবটাইটেল, লেবেলসর্বস্বতা ইত্যাদি থেকে তফাতে থাকার চেষ্টা করি । জীবিকায় শিক্ষক হবার জন্যে, এবং ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক হিসাবে আমাকে কিন্তু ওই সব পড়তে হয়েছে, এবং ক্লাসে ওই সব বলতেও হয়েছে, বিশেষত তথাকথিত নন্দনতত্বের ক্লাসে । আমাকে ক্ষমা করুন, পাঠক, ক্লাসে, প্রকাশ্যে ওই সব আমি মানিও বলতে হয়েছে, বা এই ঠিক যে রস নয় প্রকার, ছত্রিশ তার অনুষঙ্গ, যেভাবে ওই সব লেখা পোয়েটিইকস সম্পর্কিত গ্রন্হাদিতে, সেভাবেই বলতে হয়েছে । নিজের কথা বলার তো স্কোপ নেই, তাই ছাত্রদের কোনও দিনই বলা হয়নি যে, ওই সব জেনেও, সাহিত্যের চুলও ছোঁয়া যায় না ।
এমতাবস্হায় আমাকে লিখতে হচ্ছে, ওই কথা অর্থাৎ মলয় রায়চৌধুরীর পোস্টকলোনিয়ালিজম এবং তাঁর পোস্টমডার্নিজম । পাঠক অবশ্যই ভাবতে পারেন, কী দরকার ছিল এইসব ঘটা করার । স্রেফ মলয় রায়চৌধুরী কী ও কে সহজ সরল ভাষায় সরলার্থ করলেই হত !
হত না ।
কেননা পাঠক হিসেবে পাঠকমনকে যতটা জানি, সাহিত্যের আলোচনায় যদি ওই সব ইজম, টাইটেল, লেবেল না-থাকে, তাহলে অ্যাকাডেমিক সাহিত্য বুঝতে বড় অসুবিধে হয় । যেই লেখা হল, মলয় হাংরি জেনারেশন অন্যতম ইশ্যু, অমনি পাঠকের যা বোঝার সহজে বোঝা হয়ে গেল । কেননা পাঠকের, যে-কোনো ভাবেই হোক, ওই সব টাইটেল চোখে পড়বেই এবং মূর্ত থেকে বিমূর্ত ধারণা থেকেই যাবে, বলা উচিত জন্মও নেয় ওই সব ইজম, টাইটেল একবার মগজে ঢোকাতে পারলে । এখন, কী করি, আপনিই বলুন পাঠক, যখন পাঠক হিসেবে আমাদের মাথায় ইতিমধ্যেই ঢুকে বসে আছে ওই সব, তখন ওই সব দিয়েই কাজ করে যেতে হবে । না-হয় বযোজোর আমি ইজম টাইটেলের ফ্রেম ভেঙে গড়ে দিলাম । এবং এভাবে পাঠকমন ও আমার ভেঙে দেয়ার মধ্যে সত্যবস্তুকে রক্ষা, দুই-ই সামলালাম । হ্যাঁ, পাঠক, দু-নৌকোয় পা দিয়েই কাজটা করতে হবে । মানুষের সে-অভ্যাস ভালোই আছে -- কেননা পৃথিবীতে মানুষই একমাত্র তথাকথিত অনাবিল জানোয়ার হয়ে পরক্ষণেই আবার তথাকথিত আবিল মানবিক হতে পারে । এ-কাজকেই আবার মানুষই বলর দু-নৌকোয় পা দেয়া ।
দুই
যাই হোক, প্রথমে পোস্টকলোনিয়ালিজমের কথা হয়ে যাক । অর্থাৎ মলয় কোথায় পোস্টকলোনিয়াল । এ-ব্যাখ্যায় আমি মলয়ের নিজস্ব ‘ভূমিকা’ তথা ‘আত্মপক্ষ’ থেকে ওঁরই কথাগুলো হুবহু লিখে যাচ্ছি : “২৯ অক্টোবর ১৯৩৭ থেকে ২ নভেম্বর ১৯৩৯ এর মধ্যে কোনো ১১ই কার্তিক, পাটনার প্রিন্স অব ওয়েল্স মেডিকাল কলেজ হাসপাতালে, পৃথিবীর দিকে পা করে জন্মাবার’’’”ইত্যাদি । অথচ ক্ষণেক পরেই ওই মলয় জানাচ্ছেন, “হাসপাতালের রেকর্ড খুঁজে দেখেছিলুম ২৯ অক্টোবর -- ২ নভেম্বর ১৯৩৭, ১৯৩৮, ১৯৩৯ বৃহস্পতিবার শুক্রবার শনিবার কারুর, ছেলে হয়নি, হলেও মরা অবস্হায়।”--- ময় রায়চৌধুরীর ‘ভেন্নগল্প’-এর দ্বিতীয় ভূমিকার ‘প্রতিবন্ধী অস্তিত্ব’ থেকে হুবহু নেয়া ( পৃ ্ঞ-ট, মার্চ ১৯৮৪ ) ।
এখন ব্যাখ্যা সরল যে, মলয় পোস্টকলোনিয়াল, কেননা মলয় কলোনিয়াল নন, কেননা মলয় কলোনিতে জন্মাননি, কেননা পৃথিবীর দিকে পা করে জন্মাবার সুযোগ পেয়েছিলেন, কেননা পরবর্তীতে ওই হাসপাতালের রেকর্ডে, যেখানে তিনি জন্মেছেন বলে লোকশ্রুতি, সেখানে কোনও পুত্রসন্তান ( ছেলে ) জন্মাবার তথ্য নেই । অর্থাৎ মলয় পোস্টকলোনিয়াল ইন দা ট্রুয়েস্ট সেন্স অব দা টার্ম । পোস্টকলোনিয়াল না হলে নিজের প্রতিবন্ধী কলোনিয়াল অস্তিত্বকে, এবং তার পরিকাঠামোর ফ্রেম এভাবে ভাঙতে পারতেন না । মলয় এখানে অপ্রাতিষ্ঠানিক, এবং উত্তরঔপনিবেশিক । ঠিক, তদুপরি বলি, মলয়ই একমাত্র, যিনি ঘোষণা করেন, “মলয় রায়চৌধুরীর কোনো গ্রন্হের কারুর কোনো কপিরাইট নেই’...কোনোরকম স্বত্ব কারুর জন্য সংরক্ষিত নয় । তা পাঠকের।” মলয় এখানে তৃণমূল গণতান্ত্রিক, অতএব উত্তরঔপনিবেশিক । বলা বেশি হোক, তবু বলি, পাঠক, এখানেই তাঁর পোস্টকলোনিয়ালিজম বুঝুন । এই পোস্টকলোনিয়াল হবার জন্যই মলয় বড় সহজে পোস্টমডার্ন হতে পেরেছেন । অবশ্য মলয় স্বয়ং মনে করেন, সাম্রাজ্যবাদে পতনের সঙ্গে উপনিবেশেরও পতন হয় । তবুও মলয়ের জন্মকালে, বাল্যকালে, কৈশোরেও কিন্তি ওই সাম্রাজ্যবাদের ঐতিহাসিক পতন ঘটেনি ।
তিন
এবার পোস্টমডার্নিজম পপসঙ্গে যাই, কেবল এই কথা বলে নিয়ে, মলয় যে-উত্তরঔপনিবেশিক তথা অধুনান্তিক, এ তাঁর জন্মবৃত্তান্তেই আভাসিত, কেননা সেখানে সে যৌগিক সংস্কৃতির । জন্মলাভও করেন, আবার রেকর্ড রাখেন না ।
পশ্চিমী সভ্যতার এক শূন্যতায় পোস্টমডার্নিজম যে কেবল নঞর্থক প্রতিক্রিয়া, তা নয়, একটা প্রতিবাদের জায়গাও বটে । ১৯৭০ ও ৮০র দশকের সিনিসিজম ও হতাশার সঙ্গে সামঞ্জস্য বলেই এর চিন্তাভাবনা ক্রমশ প্রভাব বিস্তার করেছে । সাধারণ মানুষের অবিশ্বাস ও পরাজিত মনোভাবের ভূমিটি, পোস্টমডার্ন তত্ব, কবিতা, শিল্প অধিকার করার, সক্ষমতাতেই মনোযোগ আকর্ষণ করে । পোস্টমডানড চিনতায়, তার অন্যতম প্রধান প্রবক্তা জাক দেরিদার ভাবনায়, পাওয়ার বা ক্ষমতা সম্পর্কেই সন্দেহ ঘনীভূত, ক্ষমতার দুর্নীতিগ্রস্ত হওয়ার দিকে অঙ্গুলিসংকেত । দেরিদা বলেন, ক্ষমতা সবকিছুকে জোর করে এক করতে চায়, পার্থক্য অস্বীকার করে, সময় ও সময় ছাড়িয়ে জীবনশিল্পের নানামাত্রিক ব্যাখ্যাকে চেপে ধরে এক করতে চায়, প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্হাতেও এর ব্যত্যয় হয় না । পাওয়ারকে তাই অবিশ্বাস করো । মানুষের তুচ্ছতা ও ক্ষমতাহীনতাকে পোস্টমডার্ন সামনে নিয়ে আসে । অত্যাচারিত যে অত্যাচারিত, তার কারণ সমগ্র ব্যবস্হাই অনিবার্যভাবে অত্যাচার পুনরুৎপাদিত করে । পোস্টমডার্নে এ সত্যই ধ্বনিত হয়, ক্ষমতাবান অত্যাচারিতের ভালো তো মোটেও নয়, বরং খারাপ । শুধু তাই নয়, দেরিদা ও পোস্টমডার্নেরা মনে করেন, সক্রিয়তার কোনও নির্বাচন নেই, যে কোনও সক্রিয়তাই ক্ষমতার সামগ্রিকতায় আক্রান্ত হয়, কার্যকর সক্রিয়তা তাই অনৈতিক । স্বাধীনতা যদি পেতেই হয়, তাহলে প্রয়োজন ‘ডিকন্সট্রাকশান’-এর বা বিনির্মাণের । এখানেই মানুষ পোস্টমডার্নকে সঙ্গী হিসাবে পায় : কারণ জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতায় সে দেখে স্বাধীনতার অনুপস্হিতি, দেখে যে-কোনও রাজনৈতিক ব্যবস্হাই হোক, ফলাফল একই : হতাশা ও স্বাধীনতাহীনতা । আমাদের “বাস্তবেও অন্য প্রক্রিয়ায় প্রায় এরকমই অভিজ্ঞতা পাওয়া যায় । পোস্টমডার্নের এই সাধারণ মানুষের অসহায়তা বোধের উপর গুরুত্ব দেওয়া, এখানেও তাই প্রাসঙ্গিক মানুষের তুচ্ছ হয়ে যাওয়া, মানুষের হতাশা এ-বাস্তবেও অন্যভাবে ক্রমশ মানব অস্তিত্বকে খাচ্ছে ।”
উদ্ধৃতিটি পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের । তাঁর পোস্টমডার্নিজম তত্বের ব্যাখ্যায় ওইভাবে অগ্রসর হয়ে তিনিও জানাচ্ছেন, পোস্টকলোনিয়াল না হলে পোস্টমডার্নিজমে প্রবেশ করা যায় না অবশ্য তিনি এ কথাও বলতে ছাড়েন না, কলোনিয়াল তৃতীয় বিশ্বের যে-হতাশা প্রথম বিশ্বের দ্রুত গ্লোবালাইজেশান দেখে জন্মায়, সেখানে পরোক্ষে পোস্টমডার্ন হওয়া যায়, যদিও তা খানিক পুঁথিপড়া হবে, স্পন্টেনিয়াস হবে না । এবং এখানকার মানুষদের তুচ্ছ হয়ে যাওয়া প্রথম বিশ্বের মানুষদের দেখে, দ্রুত উল্লম্ফনের দ্বারা সব তুচ্ছতাকে কাটাবার মানসিকতায় বৈদেশিক ঋণ নিয়েও -- গ্রাম্য কলকাতায় মেট্রোরেল করা, যার শুরুতেও অদূরে গ্রাম্য আচরণ, তার শেষেও ওই আচরণ, শুরুর তুল্যই, নিকটবর্তী । অথবা হায়দ্রাবাদে প্রথম বিশ্বকেও চমকে দেবার জন্য প্রস্তুত ইন্টারনেটের মহিমা, যারও অদূরে তেলেঙ্গানার কাছাকাছি ব্রাহ্মণ্য দাপট সর্বকালের গ্রাম্যতাকে ছাড়িয়ে যায়, এখনও । অর্থাৎ আধুনিকতা এখানে আধিপত্যবাদী নয়, ভঙ্গুর । তাই পোস্টমডার্ন হওয়া যায় । কেননা গ্রাম্যতার আয়রনিকাল অস্তিত্বেই বস্তুত পোস্টমডার্নিজমের আবির্ভাব ।
আমিও এসব মানি । বলা উচিত পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ওই ভাবনাকে অভিব্যক্ত করার জন্য আমি আমারই বাক্যসমূহকে কাজে লাগাই । এবং আজ একথা স্বীকার করা আমারই দায় যে এসবই আমি, বড় সম্প্রতি, মলয় রায়চৌধুরী থেকে সম্প্রসারিত হয়েছি ।
চার
সমীর রায়চৌধুরী সম্পাদিত ‘পোস্টমডার্নিজম : অধুনান্তিকতা’ গ্রন্হের প্রবন্ধ ‘পোস্টমডার্নিজম তত্ব : মলয় রায়চৌধুরী’ আমি একাধিকবার পড়লাম । সম্প্রতি খুব মন দিয়ে এমন নিবিড় পাঠ আর করিনি । কার্যত আমি প্রকৃতই বিস্মিত হচ্ছিলাম, এমন অনাবিল প্রক্রিয়ায় এদেশে বসবাস করে কীভাবে ওই প্রবন্ধ লেখা যায় । মাইল মাইল অসহনীয় জ্ঞান তো পযেই আছে কতকাল ধরে । কবেই আমি জানিবার জানিবার গাঢ় বেদনার ভার ঘাড় থেকে নামিয়ে, বেশ বহাল তবিয়তে আছি, ওই জ্ঞান আহরণের অসহনীয় বিদীর্ণ বিস্ময় থেকে মুক্ত হয়ে । স্হির করে নিয়েছিলাম, আর ওপথে যাব না । বড় জোর প্রিয় লেখকদের গদ্য-পদ্য পড়ে যাব, তাতে হবতো বা প্রাবন্ধিকতা থেকে যেতে পারে, অথবা ওই, জ্ঞান, যা আমার সুখের চুল অব্দি ছুঁতে পারে না । তবু ওই পর্যন্তই। আমি এখন শেকসপীয়ারের সবকিছু, বিশেষত সনেট, রবীন্দ্রনাথের গল্প-উপন্যাস-গান-ছবি, জীবনানন্দের ও বিনয় মজুমদারের সবকিছু পড়ে যাই । ভেবেছিলাম, এভাবেই কাটিয়ে দেব আরও কিছুকাল । তারপর কালীপ্রসন্ন সিংহের ‘মহাভারত’ । দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামীর এপিসোডে বেদব্যাসের ম্যাজিক রিয়ালিটি । তারপর মৃত্যু অথবা মস্তিষ্কের স্তব্ধতা আসা স্বাভাবিক ।
পাঁচ
কিন্তু এখন, এই মুহূর্তে, আমি স্হির করে ফেলেছি, সঙ্গে মলয় রায়চৌধুরী পড়ে যাব । এবার হুবহু মলয়ের সেই কথাগুলো লিখে যাই :-
“আধুনিকতার কালখণ্ডটির ছিল ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ । সাম্রাজ্যবাদের উথ্থান ও পতনের সঙ্গে ঘটেছে আর্ট ফর্ম রূপে উপন্যাসের উথ্থান ও পতন । সাম্রাজ্যবাদের পতনের সঙ্গে ফুরিয়েছে আধুনিকতা ও আধুনিকতার অবসানের সঙ্গে সম্পূর্ণ ছিতরে গেছে উপন্যাসের ফর্ম । উপন্যাসের আদি কাঠামো ভেঙে পড়ার সঙ্গে কাহিনিকেন্দ্র থেকে অপসারণ ঘটেছে নায়কের । যারা যারা কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিল, সাম্রাজ্যবাদ, আধুনিকতা, উপন্যাস বা নায়ক, সবাই আক্রান্ত হয়েছে অধুনান্তিক কালখণ্ডে । কেন্দ্র থাকলে থাকবে পরিধি বা প্রান্ত বা প্রত্যন্ত । সাম্রাজ্যবাদের প্রান্তিক যেমন উপনিবেশ । আগেকার উপন্যাসে অন্ত্যজ ছিল প্রান্তিক । শহর যদি ক্ষমতার কেন্দ্র হয়, গ্রাম তাহলে প্রান্তিক । আমি কেন্দ্রে থাকলে তুমি হবে প্রান্তিক । পুরুষ যদি কেন্দ্র হয়, নারী হবে প্রান্তিক । অধুনান্তিকতা চাগিয়ে ওঠে কেন্দ্রের বিনির্মাণ থেকে । আধিপত্যকে তা খর্ব কর সাহিত্যে, সংগীতে, শিল্পে, নৈতিকতায়, রাজনীতিতে, সমাজে, ভাবদর্শে । বাংলা সাহিত্যে গোরার জায়গায় এসেছে চোট্টি মুণ্ডা ।”
“সাম্রাজ্যবাদ শেষ হবার পর উত্তরঔপনিবেশিকতা গড়ে তুলেছে নিজস্ব আগ্রহের এলাকাটি, যেটি অধুনান্তিকতার উদ্বেগজনক আগ্রহের এলাকাও বটে : প্রান্তিকতা, প্রত্যন্তবাসী, অন্ত্যজ, মফসসল, অনিশ্চয়তা, বহুচারিতা, লোকসংস্কৃতি, দোআঁশলাপনা, লালিকা, রঙের ছটা, এলোমেলো চিন্তা, যৌগিক সংস্কৃতি, অনির্ণেয়তা, আকস্মিকতা, বিশৃঙ্খলা, গৃহহীনতা, ভুতুড়ে পুঁজি, প্যাসটিশ, পণ্য, বহুত্ববাদ, ঠিকেদারি শ্রমিক চুক্তি, একযোগে অনেক কাজ, অপ্রাতিষ্ঠানিকতা, রূপের বৈচিত্র্য ও অজস্রতা, তৃণমূল গণতন্ত্র, পাড়ার নান্দনিকতা ইত্যাদি। উত্তরঔপনিবেশিকতা ও অধুনান্তিকতা মনে করে ইতিহাস একরৈখিক নয়, ইতিহাস অজস্র ও স্হানিক । সাম্রাজ্যবাদ, আধুনিকতার নামে যে ইশারা ও দ্যোতকগুলো নেটিভদের ওপর চাপিয়েছিল, সেগুলোকে অধুনান্তিকতার মাধ্যমে উপড়ে ফেলে দিতে চায় উত্তরঔপনিবেশিকতা । নেলো রিচার্ডস বলেছেন যে, ইউরোপ আমেরিকায় পোস্টমডার্নিজম সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা শুরু হবার আগেই অধুনান্তিকতার আসল প্রবণতাগুলো প্রাক্তন উপনিবেশগুলোয় চোখে পড়ে । কোনো উপনিবেশের ভাষাকে অপ্রভাবিত রাখেনি ইউরোপ । আধুনিকতার নামে চাপানো সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি, ধর্ম বিষয়ে ধারণা সবই ইউরোপের । সাম্রাজ্যবাদের শিকারটির সমস্যা, অতএব, অধুনান্তিক । তার ভাষার ভিত্তি নষ্ট হয়ে গেছে । বিচার, বিবেচনার মাধ্যম নষ্ট হয়ে গেছে । অভিব্যক্তির কাঠামো নষ্ট হয়ে গেছে । অথচ সাহিত্য ও রাজনীতিতে, উত্তরঔপনিবেশিকতা আবর্তিত হয় ভাষাকে কেন্দ্র করে, কেননা, আত্মপরিচয় অন্য কোথাও পাওয়া যায় না । দেখা যাবে যে, শিল্পে ও সাহিত্যে একই ধরণের কাজ হচ্ছে উপনিবেশগুলোয় এবং পোস্ট-ইনডাসট্রিয়াল আমেরিকায় । এশিয়া আফ্রিকা লাতিন আমেরিকায় অধুনান্তিকতার প্রাসঙ্গিকতা এ থেকেই টের পাওয়া যায় । সাম্রাজ্যবাদের দরুণ উপনিবেশের নেটিভদের স্মৃতিবিপর্যয় ঘটে গেছে । পোস্টমডার্ন লেখালিখি ও ছবি আঁকায় যে প্রবণতাগুলো প্রখর তা তুলনীয় স্মৃতিবিপর্যয়ের সঙ্গে ।”
“আমাদের দেশে বেশ কয়েকটি পোস্টমডার্নিস্ট প্রবণতা দেখা যাচ্ছে । কোনটা ঠিক আর কোনটা বেঠিক তা নিয়ে চলছে বিরামহীন খেয়োখেয়ি । সত্য, জ্ঞান, বৈধতার নানান রকমফের । যেমন উলফা, জেকেএলএফ, খালিস্তান, শিবসেনা, আমরা বাঙালি, ঝাড়খণ্ড, গোর্খাল্যাণ্ড, বোড়ো্যাণ্ড, উত্তরাখণ্ড, ইত্যাদির মতন ছোট ছোট ছাতার স্হানিক কেন্দ্রিকতা-বিরোধী চেতনা । যেমন ভূমিসেনা, লাচিত সেনা, কুঁয়র সেনা । যেমন অজস্র নাটকের দল । যেমন আঞ্চলিক ভাষার কবিতা । যেমন টুকরো টুকরো মহাআখ্যানবাদী মার্কসিস্ট-লেনিনিস্ট দল । যেমন রাজনীতিতে ক্রিমিনালদের দৌরাত্ম্য । যেমন সুমন-নচিকেতা-মৌসুমীর সংগীতের ক্ষমতাকেন্দ্র-বিরোধী গান । যেমন হাজার হাজার লিটল ম্যাগাজিন । এবং ঘরে ঘরে ‘আদর্শের শেষ’ । যেমন টিনশেড কোচিং ক্লাস শিক্ষা কাঠামো । যেমন প্রতিটি বাঙালির আঙুলে এনলাইটেনমেন্ট-বিরোধী গ্রহরত্ন । যেমন লোকনাথ বাবা, সত্য সাইবাবা, অনুকুল ঠাকুর, বালক ব্রহ্মচারী, আনন্দময়ী, দাদাজী, রজনীশ, মহেশ যোগী ইত্যাদি ধর্মের ছোট ছোট ছাতা যযা হিন্দু শুদ্রকেও প্রতিষ্ঠা দেয় । কম্যুনিটির ভাঙন এবং অ্যসোসিয়েশান সমূহের জন্ম, যে উত্তরাধুনিক বৈশিষ্ট্যের কথা কিথ টেস্টার বলেছেন, এখানে তা ঘটেছে দেশভাগের দরুণ এবং মহাআখ্যানবাদী পার্টি রাজনীতির কারণে । কৌমসমাজ ভেঙে যাবার কারণেই পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র আজ ছুতোর গয়লা নাপিত ধোপা ধুনুরি মুচি, এরা অবাঙালি।”
“গ্রামকেন্দ্রিক নৈরাজ্য গড়ে উঠেছে রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যেই । আধুনিকতার অসুখ সারানো যাবে কিনা বলা মুশকিল । এই যে দাদা একটু সরুন, দাদু ভাড়াটা দিন, মাসি বেগুন কত করে, বলার সময়ে আমরা যে শুধু দাদা-দাদু-মাসির সম্পর্কচ্যুতি জানতে পারি তা নয়, আমরা টের পাই কৌমসমাজ ভেঙে যাবার খবর, আমরা টের পাই কীভাবে এই শব্দগুলোর ভেতর থেকে তাদের মানে বের করে ফেলে দিয়েছে সমাজ । পোস্টমডার্নিজমকে বাঙালির দোরগোড়ায় এনেছে বঙ্গসংস্কৃতির অধুনান্তিক পার্টি রাজনীতি এবং উত্তরঔপনিবেশিক আর্থিক দুর্গতি।”
ছয়
এবার মলয়ের কথাগুলি নিয়ে কিছুক্ষণ ভাবা যায় । প্রথমেই বলা ভালো, আমি যে লিখেছিলাম, পোস্টকলোনিয়াল না হলে কেউ পোস্টমডার্ন হতে পারে না, সেখানে মলয়ের বক্তব্য ওই পোস্টকলোনিয়ালিজম এবং পোস্টমডার্নিজম আসলে একই বস্তুকেন্দ্রের দুটি অভিব্যক্তি, পরস্পর নির্ভর অথবা পারস্পরিক কিংবা যমঝ । অবশ্য মলয় আরও লজিকালি কথাটার বিস্তার ঘটিয়েছেন । তাঁর ধারণা, সাম্রাজ্যবাদের পতনের সঙ্গে সঙ্গে মডার্ন যুগের অবসান ঘটেছে, আধুনিকতার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে উপনিবেশেরও অবসানের লক্ষণাদি মূর্ত হয়েছে।
মলয়, বোধহয়, ধ্রুপদী সাম্রাজ্যবাদের অবসানের মধ্যেই সাম্রাজ্যবাদের চারিত্রিক অবসান দেখেছেন । আমি অবশ্য বরাবরই নিয়ো-ইমপিরিয়ালিজম টের পাই, এখনও পাই । নিয়ো-ইমপিরিয়ালিজমের অস্তিত্ব মেনে নিলেও, মলয়ের একটি কথা তবু সত্য হয়ে ওঠে । ধ্রপদী সাম্রাজ্যবাদের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ধ্রুপদী উপনিবেশেরও অবসান ঘটেছে । এটা ঠিক । এবং মলয়কে সেলাম জানাই, আমার মধ্যকার এক নিগূঢ় জিজ্ঞাসা, যার উত্তর নানা সময়ে পেয়েও আবার জিজ্ঞাসায় আক্রান্ত হয়েছে আমার মন, অর্থাৎ আমার মস্তিষ্ক, সেখানে মলয়, সম্প্রতি, তাঁর রচনাদি পাঠকালে আমার শিক্ষক হয়েছেন । অর্থাৎ যথার্থ উত্তর দিয়েছেন, যার পর আর নাই ।
একদা আমি তিন কমিউনিস্ট পার্টির কখনও সদস্য, ককনও দরদি মেম্বার হয়ে বার বার নানা মিটিং, কংগ্রেস, পার্টি ক্লাস করে যে-প্রশ্নে মন তথা মস্তিষ্ককে জেরবার করেছি, তা হল, আমাদের দেশের রাষ্ট্রচরিত্র বিশ্লেষণে ও বৈপ্লবিক স্তর নির্ণয়ে ওই নিয়ো-ইমপিরিয়ালিজম ও নিয়ো-কলোনিয়ালিজমের ভূমিকা খুঁজতে । বার বার ভুল হয়ে গেছে । সি পি আই ও সি পি এম বাহিত হয়ে যখন নয়া-সংশোধনবাদ-বিরোধী শিবিরে গিয়েছি, তখন যেন সঠিক বৈপ্লবিক পথের দিশা পেয়ে উৎসাহিত তথা আহ্লাদে আটখানা হয়ে প্রকৃতই গৃহে বাস করেও রণাঙ্গনের মাঠে যাবার উদ্যোগ নিচ্ছিলাম । সে-সময় সংশোধনবাদী সি পি আই ও নয়া-সংশোধনবাদী সি পি এম-এর মধ্যপন্হাকে ঘৃনায় বর্জন করে যখন প্রায় গৃহত্যাগে মনস্হির করচি, এমন সময়ে আমার লেখকসত্তা, যার ভিতরে কল্পনা ও যে-কল্পনার ভিতরে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার স্বতন্ত্র সারবত্তা চরাচরের নানা সম্পর্কে আসছিল, যে-সত্তা ইহলোক স্বপ্নলোকের বর্ডার মানেনি, সে সহসা দেখল, প্রকৃত রণাঙ্গন নেই । অর্পিত তথা অ-লৌকিক রণাঙ্গন আছে কেবল । তখন ওই ধারাবাহিক সত্তা, যা একান্ত আমার, আমার চিন্তা জ্ঞানলব্ধ, পুনর্বার নয়া-উপনিবেশ ও নয়া-ফিউডাল তত্বে মনোনিবেশ করল ।
এই সময়ে তথাকথিত তৃতীয় কমিউনিস্ট পার্টির অফিশিয়াল অথবা কংগ্রেসসিদ্ধ অস্তিত্ব আসেনি । তখন নানা গ্রুপ, নানা কর্মচিন্তা মাথা তুলছিল, তার মধ্যে মতাদর্শগত বিতর্কে এক ধরণের গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতাও মাথাচাড়া দিচ্ছিল । সেই উত্তপ্ত দাবানলী সময়ে আমার সঙ্গে একটি গ্রুপের যোগাযোগ ঘটে, ইতিহাসে তাদের নাম নয়া-সংশোধনবাদবিরোধী সোশ্যালিস্ট রিভলিউশানারি, সংক্ষেপে এস আর গ্রুপ । তাদের সঙ্গে দিনের পর দিন তর্কে যে জায়গায় পৌঁছেছিলাম, তার সঙ্গে মলয়ের বিশ্লেষণের গুণগত সাদৃশ্য আছে । সেই জায়গাটি হল, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ক্ল্যাসিকাল ইমপিরিয়ালিজম তথা মনোপলি ক্যাপিটালিজমেরও অন্তিম সময় উপস্হিত । অতএব উপনিবেশেরও অবসান । স্তালিন তো এই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ইমপিরিয়ালিজমের বিরুদ্ধে ঔপনিবেশিক দেশগুলির উৎসাহিত মুক্তিযুদ্ধের সম্ভাবনা দেখেছিলেন । এশিয়ায় সেই মিক্তিযুদ্ধ দুই বিশাল দেশ ভারতবর্ষ ও চিনে ততদিনের মধ্যে সূচিত হয়ে গেছে । এই বাংলার তথাকথিত এস আর গ্রুপ বলতে শুরু করেছে তখন, পঞ্চাশের দশকের শেষে, তথাকথিত স্বাধীনতা সংগ্রাম বা মুক্তিযুদ্ধে জাতীয় বুর্জোয়ার উথ্থানে, এদেশে এক উল্লম্ফনে জাতীয় বুর্জোয়ারা নয়া-সাম্রাজ্যবাদী হয়ে গেছে, অন্তত তাদের সম্প্রসারণ তথা আগ্রাসী মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে ওই তথাকথিত স্বাধীনতা সংগ্রামে । সংগ্রামান্তে, জাতীয় বুর্জোয়ার অন্যতম নেতা, তথাকথিত গণতান্ত্রক জওহরলাল নেহেরু তাঁর ‘ডিসকভারি অব ইন্ডিয়ার’ পাতায় পাতায় অনুশীলন করছেন এক বৃহৎ ভারতবর্ষ, এক উপমহাদেশের ।
ক্ল্যসিকাল সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশদের দ্বারা অধিকৃত কাশ্মীর, অসম ইত্যাদি ভারতীয় মেইনস্ট্রিমের অন্তর্গত না হয়েও তথাকথিত স্বাধীন ভারতবর্ষের ম্যাপে একান্ত ভারতীয় হিসেবে চিহ্ণিত করেছেন ওই ডিসকভারার । জাতীয় বুর্জোয়ার ভ্রূণেই সম্্রসারণবাদী নয়া-সাম্রাজ্যবাদীর ম্যাচিওর হওয়া । অতএব ওই এস আর গ্রুপের মতে, ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা এখন সম্পপসারণবাদী বুর্জোয়াদের হাতে । অর্থাৎ এই দেশের ঔপনিবেশিক মুৎসুদ্দি বুর্জোয়ার ভ্রূণে শৈল্পিক বুর্জোয়া তথা নয়া-পুঁজিবাদের ম্যাচুরিটি ঘটে গেছে । সুতরাং এখন এদেশের মূল দ্বন্দ্ব পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্হার সঙ্গে সর্বহারা শ্রমিকমনস্ক জনগণের দ্বন্দ্ব । অর্থাৎ বৈপ্লবিক স্তর হল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব । ওই সব তথাকথিত পিপলস ডেমোক্র্যাটিক রিভোলিউশান ফালতু কথা -- রণাঙ্গনে এখন পুঁজিবাদ বনাম সর্বহারা ।
মলয়কে সেলাম, প্রকৃতই সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটে গেছে । আধুনিক যুগ তার অন্তিম কালে শেষ চেষ্টা করে যাচ্ছে মডার্ন থাকার । কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের পতনের সঙ্গে সঙ্গে পোস্ট-ইনডাসট্রিয়াল যুগের সূচনা মূর্ত হতে চলেছে । এবং পোস্টইনডাসট্রিয়ালিজম আসলে ইনডাসট্রিয়াল তথা মডার্ন এজের অন্তিমে উপস্হিত হয় । এবং এটি একটি গ্লোবাল উদ্যোগ ।
সুতরাং পোস্টমডার্নিজম তার নিজস্ব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে নানা ঢঙে সব দেশেরই দোরগোড়ায় কমবেশি উপস্হিত । সেলাম মলয় । আপনি ঠিকই দেখেছেন ।
সাত
সবকিছু ছেড়ে আমি কেবল মলয়ের ‘ভেন্নগল্প’ গ্রন্হটি দেখি, কেননা পোস্টকলোনিয়াল তথা পোস্টমডার্ন চরিত্র ওই ‘ভেন্নগল্পে’ বড় স্পষ্ট, ক্লিয়ার, সমুজ্জ্বল । ভূমিকায় মলয়ও বলেছেন : ‘দেখা যাবে, এই গ্রন্হটির পাঠবস্তুগুলো কেন্দ্রহীন ; বাস্তবতাকে বিনির্মাণ করে পাওয়া স্হিতিগুলো সমন্বয়হীন ; বিষয় অথবা আঙ্গিকে ঐক্য এবং সমাপ্তি নেই এবং কাঁচামালগুলো থেকে নির্মিত হচ্ছে না কোনোকিছু ; আমি কোনো অভিপ্রায় ছাপিয়ে দিচ্ছি না । বা গড়ে দিচ্ছি না শব্দব্যূহ ।...শরীর ও মন দুটো আলাদা আলাদা ব্যাপার, এরকম সরলীকরণের মধ্যে আমি কোনো রচনাকে টানিনি । লেখাগুলো বরং ভঙ্গুরতার স্বীকৃতি হিসেবে বর্ণনাকারীর, উত্তরঔপনিবেশিক মতদ্বন্দ্বের, জটিলতার, একরকম আলাপচারিতা ।’
এখানে আমি ওই ভূমিকায় যুক্ত করতে চাই ওই ‘উত্তরঔপনিবেশিক’-এর সঙ্গে ‘উত্তরআধুনিক’ শব্দ, যে দুই শব্দ, পূর্বেই লিখেছি, যমজ ।
‘ভেন্নগল্প’-গ্রন্হের প্রথম প্রকাশ কলকাতা বইমেলা ১৯৯৬ । রচনাকাল ১৯৮৩ - ১৯৯৫ । আমি ওই রচনাকালের মাঝামাঝি রচিত, ১৯৯২ সালের ‘অলৌকিক দাম্পত্য’ গল্পটিকেই কেবল ধরে মলয়ের পোস্টকলোনিয়াল, মলয়ের পোস্টমডার্ন চরিত্র বোঝার চেষ্টা করব ।
কেননা গল্পটি প্রতিনিধিস্হানীয় । আমার কাছে অসাধারণ । গল্পটির শুরু ও শেষ অনাদি ও অন্তহীন ।এবং আসলে গল্পটির মধ্যে কোনো স্টোরি এলিমেন্ট নেই । বলা উচিত এটি গল্প নয়, গদ্য ছাড়া আর কোনও অভিধা আমার জানা নেই । মলয়ের মতে Post-colonial episodes/Texts ; সবকিছুই বিনির্মাণের পর অভিব্যক্ত । শব্দগঠন বিনির্মিত । বাক্যবিন্যাস অব্দি বিনির্মিত । এই গদ্যের কোনো কেন্দ্র নেই, অতএব কোনো গ্রহ বা উপগ্রহ নেই ।
আট
তবে অন্যান্য গদ্য রচনাও আলোচনার মধ্যে আনলে ভালো হতো । সময় ও সুযোগের অভাব । পরন্তু আমার স্বভাবও এই যে, আমি নানা কিছুর মধ্যে আলোচনাকে বিন্যস্ত রাখতে পারি না । আমার পক্ষে সহজ একটি দুটির মধ্যেকার কথানুসন্ধান । যেমন ধরুন, কবিতা নাটক পুরো তফাতে রাখছি আপাতত । এমনকি বলা যায় উপন্যাসও, যদিও ‘নামগন্ধ’ উপন্যাসটি মাথায় থেকেই যাচ্ছে, জানি না কেন ! শুধু এটুকু জানি, মলয়ের পোস্টকলোনিয়াল তথা পোস্টমডার্ন সিনট্যাক্স নিয়ে যে ভাবনা গড়ে উঠল এই কদিনে, তাতে ওই ‘নামগন্ধ’ উপন্যসের কিছু ভূমিকা আছে । মলয়ের মালমশলা ছড়িয়ে রেখেছি চতুর্দিকে, এবার কেবল বেছে নেবার পালা । তাতে ওই ঘটল, ওই ‘অলৌকিক দাম্পত্য’ ।এই ‘অলৌকিক দাম্পত্য’-এর অন্তর্গত নয়, অথচ সঠিক বাইরেও নয়, এমনকিছু আপাত অপ্রাসঙ্গিক, কিন্তু যথার্থই পপাসঙ্গিক কথা হয়ে থাক ।
মডার্ন যুগের মার্কসীয় রাজনীতির এক চমৎকার পোস্টমডার্ন অভীপ্সা আছে । গদ্যটির নাম ‘ভেন্ন’, সেখানে সীতেশের তারিখবর্জিত ডায়েরির লেখাটা :-
“আজকাল আমাদের দেশে শ্রেণিচেতনা বলতে সাধারণত পুঁজিপতি জোতদার ধনী ব্যক্তি প্রভৃতির বিরুদ্ধে জঙ্গী মনোভাবকে বোঝানো হয়ে থাকে । এটা শ্রেণী চাতনার একটা স্হুল দিক মাত্র । আসলে শ্রেণীচেতনা হল সমাজের বস্তুবাদী বিশ্লেষণের ভিত্তিতে সমাজ বিকাশের পথ অনুধাবন করে ওই মুহূর্তের প্রগতিশীল কর্তব্য নিরুপণ করার ক্ষমতা । এক্ষেত্রে মার্কসবাদের চিরায়ত তত্ব ও সংক্ষিপ্ত মূল সূত্রগুলি খুব বেশি সহায়ক হবে না । বরং মার্কসবাদী পদ্ধতির সৃষ্টিশীল প্রয়োগের মাধ্যমেই যে কোনও দেশের পরিস্হিতির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ সম্ভব । এবং মার্কসবাদী সমাজ বিশ্লেষণের মূল কথা হল, ঐতিহাসিক বিকাশের পটভূমিতেই যেকোনো সমাজের বিশ্লেষণ করতে হবে ।”
‘ভেন্ন’ গল্পটি কিন্তু ১৯৮৩ সালে লেখা । অর্থাৎ ওই আশির দশকের গোড়ার থেকেই মলয়ের পোস্টমডার্নজম কাজ করছে ।
এখানে ‘The Name Of The Rose’, যা একটি পোস্টমডার্ন উদ্যোগ, তার লেখক উমবের্তো একোর কিছু কথায় আসি…”it ( postmodernism ) demands, in order to be understood, not the negation of the already said, but its ironic rethinking.” মলয় লিখিত ওই ডায়েরি, পাঠক বুঝুন, not the negation of the already said, but its ironic rethinking.
নয়
এবার সত্য সত্যই ‘অলৌকিক দাম্পত্য’র চাবিকাঠি পেয়ে গেলাম । কেননা এই গদ্য, বস্তুত, দুর্ঘটনা, যা আকছার ঘটছে, তারই ironic rethinking । দুর্ঘটনা, এখানে বাস দুর্ঘটনা, মলয়ের সৃষ্টিশীল প্রয়োগে যে-দুর্ঘটনা অলৌকিক, তাই বলে অ-লৌকিক নয় । দাম্পত্যের যে কথা এখানে আছে, তাও ironic rethinking ।এখানে বলে রাখা ভালো, মডার্ন যুগেই দাম্পত্যের শেষ দেখা গেছে । লিভ টুগেদার মডার্ন সমাজ মেনে নিয়েছে । পোস্টমডার্ন সমাজ তারই ironic rethinking দেয় বলে ধারণা করি । এক্ষণে সরাসরি মলয়ের বাক্যে আসি :-
“কুড়ি বছর আগে শহরের উদাসীন রেল স্টেশনের সামনে চকচকে দুপুরের রাস্তায় কুড়িয়ে পেয়েছিলুম ফরসা যুবতীর কাটা তর্জনী, রক্তহীন, কাচের রঙের নীলচে নখপালিশ, সোনার অলস আঙটিতে গরম পদ্মরাগমণি ঠায় জেগে…”
এবার, এই মলয়, কে বা কী, যিনি ওই অলৌকিক তর্জনী কুড়িয়ে পেলেন ? মলয় স্বয়ং বলেছেন, ওই পদ্মরাগমণি তো আসলে চুনি, এবং---
“যে চুনিতে আজও গ্রীষ্মকালীন কেনিয়ার বহুচারী যুবক সিংহের থাবার থমথমে গন্ধ আমাকে দু’তিনশো বছর আগে ফিরিয়ে নিয়ে যায়, যখন আরা বালিয়া বা ছাপরা থেকে আমার কেঁদো পূর্বপুরুষরা পাকানো চামড়ার চাবুক খেতে আর অর্ধাহারে থাকার জন্যে কালোদের দ্বীপে জাহাজবন্দী কেনা গোলাম হয়ে চলে গিয়েছিলেন।”
এখানে মলয় প্রকৃতই বিশ্ববাসী তথা আবহমানকালীন । এখানে সময় ও কালের বিনির্মাণ হচ্ছে । এটি একটি পোস্টমডার্ন উদ্যোগ । আবার দেখুন, দুর্ঘটনাগ্রস্ত মলয় ও তাঁর সহযাত্রীদের, ইতস্তত মৃত, অথবা জ্ঞানরহিত স্টেজের বিনির্মাণ । যেমন :-
“যে-দুটো রূপসী শীতল হাত আমাকে পেছন থেকে নির্লজ্জ জড়িয়ে রয়েছে, নারীর আতর মাখা বাহু, সোনার কয়েকগাছা অমৃতসরী চুড়িসহ, আজকে, কুড়ি বছর পর, এই শীতের আধো অন্ধকার সকালে, সে-হাতের দক্ষিণ তর্জনীতে সেই হুবহু আঙটি পদ্মরাগমণি । চল্লিশোর্ধ অকৃতদারকে এভাবে আকুল আঁকড়ে থাকা রহস্যময়ী বাহু, এতো শক্ত করে ধরে থাকা, আমি পেছন ফিরে দেখার চেষ্টায় ঠাহর করতে পারলুম না ।”
এবার পাঠক দেখুন, কুড়ি বছর আগে পাওয়া তর্জনী, এখন এই দুর্ঘটনার বিনির্মাণে রূপসীর অঙ্গীভূত । এবং তর্জনীতে । রহস্যময়ী বাহু ধীরে ধীরে অলৌকিক দাম্পত্যে নিয়ে যাচ্ছে । সে এক অসাধারণ বর্ণনা । এবং সে-বর্ণনাও মডার্ন ন্যারেটিভকে বিনির্মাণের মধ্য দিয়ে পোস্টন্যারেটিভ ডিসকোর্সে নিয়ে যাচ্ছে । যেমন:-
“---ভাগ্যিস আপনি মারা গেলেন, তাই আপনার সঙ্গে এই নিবিড় পরিচয়ের সুযোগ পেলুম।” আমি বললুম ওঁকে, শীতের নিরাপদ ফিকে সকালকে শুনিয়ে, যখন আশেপাশে সবাই মরে গেছে মনে হয়, শুধু আমি বেঁচে, আমদের অমোঘ খবর কেউ জানতে পারেনি।”
“আপনার হৃদয় স্তব্ধ হয়ে গেছে । আপনি আমার কথা ভাবছেন না । কিন্তু তবু কেন ভালোবাসছেন আমায় ?”
“........”, আমি ওঁর আলতো করে বলা কথাগুলো শুনতে পাই । নিঃশব্দ কল্লোল হয়তো এই, অভিব্যক্তিহীন কাকলি, স্খলিত কেকা ।
“........”, উনি অজস্র কথা বলে যেতে থাকেন ।
“.........”, চোখ বন্ধ করে শুনি ওঁর কথাগুলি । মাথা পেছনে করে ওঁর ঠাণ্ডা ঠোঁটে আমার গাল ঠেকাই ! আমার উত্তাপ ওঁকে মুগ্ধ করে ।
আমিও বলে যেতে থাকি ।
-----বেঁচে থাকতে আমাকে চেয়েও দেখতেন না হয়তো আপনি ।
-----কতোদিন ভেবেছি আপনার কাটা আঙুল আর আঙটি আপনাকে খুঁজে ফেরত দিয়ে আসব ।
-----এখন তো আপনি আমার ভাষাও বুঝতে পারছেন না । না ?
-----বাসে, প্রতিটি মেয়েমেনুষকে বারবার দেখেছিলুম, কিন্তু কই, দেখিনিতো আপনাকে ।
-----আমার সৌভাগ্য, এতো লোক থাকতে আমাকেই আপনি বেছে নিলেন, এক বিচারাধীন মধ্যবয়সীকে ।”
পাঠক, দেখুন, এখানে, মডার্ন ডায়ালগের বিনির্মাণ, যা কিনা পোস্টমডার্নিজমের অন্যতম কোয়ালিটি । এ গদ্যে ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমিও আছে ।
পোস্টমডার্নিজম তো অতীতকে, অতীতের রূপকথাকেও আহরণ করে, কিন্তু আয়রনিকালো ওই কার্য সম্পন্ন হয় । দেখুন :-
“ব্যঙ্গমি : ওকে ফিরে যেতে হবে ।
ব্যঙ্গমা : কোথায় ?
ব্যঙ্গমি : লাৎখোরদের পৃথিবীতে । বিপ্লবে । সংঘর্ষে । পরাজয়ে । সেখানে হাতিশালে হাতির গু থাকে, ঘোড়াশালে পড়ে থাকে লোহার নাল । ছাদের ওপর নৌকো, সিংহাসনে গাধা, নহবতখানায় কাক, মন্ত্রণাঘরে মাকড়সা, কোষাগারে গোবর, কামারশালে নেহাইয়ের ওপর ছাইভস্ম, পালঙ্কে আরশোলা, বাঁশের সাঁকো দিয়ে তৈরি রামধনু, গেরস্ত বাড়িতে ঘরে ঘরে ধেনো-টানা মাতালচি, খোরপোষের টাকায় প্রতিপালিত রাজনীতিক, মৃতদেহের বদলে মুখাগ্নি করার তোষক ।”
পাঠক, লক্ষ করুন, আধুনিকতাকে লাথি মেরে অধুনান্তিকতার অন্যতম লাৎখোর মলয়কে কোথায় ফিরে যেতে বলা হচ্ছে । ওই সব বিনির্মিত শব্দসমূহে আপনি অর্থ খুঁজতে পারেন, কিন্তু তাতে যেন বিনির্মিত অর্থ হয় । কেননা পোস্টমডার্নরা, স্বাভাবিক কারণেই, মডার্ন ভাষাতত্বকে অতিক্রম করে যান ।
দশ
পাঠক, এই ‘অলৌকিক দাম্পত্য’ গদ্যে যে-যৌনতা আছে, তাও মডার্ন যৌনতারই বিনির্মিত যৌনতা, যা পোস্টমডার্ন । এ-বিষয়ে পোস্টমডার্ন William Simon যা বলেছেন, তা শুনুন, “For many people, the sexual part of their lives will take on new and somewhat disruptive salience -- disruptive in the sense that the metaphoric richness of the sexual may have to risk real life testa, tests that involve the effort to bring one’s fantasies into one’s reality. Such efforts have commonly led either to crises or to an impoverishment of both fantasy and reality.”
‘অলৌকিক দাম্পত্য’ এখানেই সত্য । এ-গদ্যে ফ্যান্টাসি-রিয়্যালিটি একবার বিন্যস্ত, তন্মুহূর্তেই ডিকনসট্রাকটেড । একবার ব্যথিত, তন্মুহূর্তেই নির্বেদ ।
আর এখানেই পোস্টকলোনিয়াল-মলয় এবং পোস্টমডার্ন-মলয়, এই বাংলায়, অদ্যাপি, সার্থক ও তুলনারহিত । সেলাম মলয় ।
[ এপ্রিল, ২০০১ ]
 মলয় রায়চৌধুরী | 122.179.172.247 | ২৪ আগস্ট ২০২১ ১৯:৩৩734903
মলয় রায়চৌধুরী | 122.179.172.247 | ২৪ আগস্ট ২০২১ ১৯:৩৩734903অভিশপ্ত কবি : পল ভেরলেন
মলয় রায়চৌধুরী
‘পোয়েত মদি’ ( Poète maudit ) বা ‘অভিশপ্ত কবি’ নামে ১৮৮৪ সালে ফরাসি প্রতীকবাদী ও ‘ডেকাডেন্ট’ কবি পল ভেরলেন একটি বই প্রকাশ করেছিলেন । অভিধাটি ১৮৩২ সালে প্রথম ব্যবহার করেন অ্যালফ্রেদ দ্য ভিনি ( Alfred de Vigny ) তাঁর ‘স্তেলো’ উপন্যাসে ; তিনি বলেছিলেন ‘পোয়েত মদি’ হিসাবে চিহ্ণিত লোকগুলোকে জগতের ক্ষমতাধর মানুষেরা চিরকাল অভিশাপ দেবে। ত্রিস্তঁ করবিয়ের (Tristan Corbière ) , জাঁ আর্তুর র্যাঁবো, স্তেফান মালার্মে, মারসেলিঁ দেবোর্দে-ভামো ( Marceline Desbordes-Valmore ) এবং আগুস্তে ভিলিয়ার্স দ্যলিজলে আদঁকে ( Auguste Villiers de l'Isle-Adam ) পল ভেরলেন চিহ্ণিত করেছিলেন অভিশপ্ত কবি হিসাবে । এই তালিকায় তিনি নিজেকেও অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন পুভ লেলিয়ান ( Pauvre Lélian ) ছদ্মনামে । উল্লেখ্য যে ১৮৮৪ সালে স্ত্রী মাতিলদে ভেরলেনকে আইনত ডিভোর্স করেছিলেন ।
পল ভেরলেন তাঁকে ‘অভিশপ্ত কবি’ সংকলনে অন্তর্ভুক্ত করার আগে ত্রিস্তঁ করবিয়ের ( ১৮৪৫ - ১৮৭৫ ) ফরাসি আলোচকদের কাছে সম্পূর্ণ অবহেলিত ছিলেন ; বহুকাল পরে এজরা পাউণ্ড ও টি. এস. এলিয়ট তাঁর কবিতা বিশ্লেষণের পর ত্রিস্তঁ করবিয়েরকে কাব্যসাহিত্যে গুরুত্ব দেয়া আরম্ভ হয় । করবিয়েরের মা, মারি-অঞ্জেলিক-আসপাসি পুয়ো’র বয়স যখন উনিশ তখন করবিয়েরের জন্ম হয় । তাঁর বাবা আঁতোয়াঁ-এদুয়া করবিয়ের ‘লে নেগরিয়ের’ নামে একটি উপন্যাস লিখেছিলেন । রাজকীয় উচ্চবিদ্যালয়ে ১৮৫৮ থেকে ১৮৬০ পর্যন্ত পড়ার সময়ে তিনি ডিপ্রেশনে আক্রান্ত হন এবং রিউমেটিজমের কারণে হাত-পা বিকৃত হয়ে যায় । বাড়ি থেকে অনেক দূরে স্কুলে দেবার এবং শারীরিক বিকৃতির দরুন তিনি বাবা-মাকে দোষ দিতেন । স্কুলের কড়া নিয়মনীতি ও শিক্ষদের প্রতি ঘৃণা তাঁর কবিতায় একটি বিশেষ কন্ঠস্বর গড়ে দিতে পেরেছে।করবিয়ের মারা যান যক্ষ্মারোগে, মাত্র তিরিশ বছর বয়সে । করবিয়েরের একটি কবিতা :
বিপরীত কবি
আরমোরিকার সাগরতীরে । একটি নির্জন মঠ ।
ভেতরে : বাতাস অভিযোগ করছিল : আরেকটা হাওয়াকল ।
এলাকার সমস্ত গাধা বীজসুদ্ধ আইভিলতায় তাদের দাঁত ঘষতে এসেছিল
ফুটোয় ভরা এমনই এক দেয়াল থেকে যা কোনও জীবন্ত মানুষ
দরোজার ভেতর দিয়ে ঢোকেনি।
একা— তবু নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে, ভরসাম্য বজায় রেখে,
একজন বুড়ির থুতনির মতন ঢেউখেলানো
তার ছাদ কানের পাশে চোট দিয়েছিল,
হাবাগবা মানুযের মতন হাঁ করে, মিনারটা দাঁড়িয়েছিল ।
অভিশপ্ত কবি জাঁ আর্তুর র্যাঁবোর ( ১৮৫৪ - ১৮৯১ ) কবিতার সঙ্গে পাঠকরা পরিচিত ; তাঁর ‘ইল্যুমিনেশানস’ বইটির নামকরণ করেছিলেন পল ভেরলেন । বইটি থেকে ‘শহর’ শিরোনামের গদ্যকবিতা :
এক মহানগর যাকে এই জন্যে আধুনিক মনে করা হয় যে বাড়িগুলোর বাইরের দিক সাজানোয় আর নগরের পরিকল্পনায় প্রয়োগ করার জন্য পরিচিত উপলব্ধিগুলো এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে ; তারই আমি এক ক্ষণজীবী আর তেমন বিচ্ছিন্ন নাগরিক নই । এখানে তুমি কুসংস্কারের একটিও স্মৃতিস্তম্ভের হদিশ পাবে না । সংক্ষেপে, নৈতিকতা আর ভাষাকে সরলতম প্রকাশে নামিয়ে আনা হয়েছে ! লক্ষাধিক এই লোকজন যারা পরস্পরকে জানার প্রয়োজন অনুভব করে না, নিজেদের শিক্ষাদীক্ষা, কর্মকাণ্ড, বার্ধক্যে এতো মিল যে তাদের আয়ু মহাদেশের গোলমেলে সংখ্যাতত্ব যা বলেছে তার চেয়েও বেশ কম । তাই, আমার জানালা দিয়ে, দেখতে পাই নতুন প্রেতরা শাশ্বত ঘন ধোঁয়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছে --- আমাদের বনানীঘেরা ছায়া, আমাদের গ্রীষ্মের রাত ! -- প্রতিহিংসর নতুন গ্রিক দেবতারা, আমার কুটিরের সামনে, যা আমার স্বদেশ, আমার সমগ্র হৃদয়, কেননা এখানে সবকিছুরই পরস্পরের সঙ্গে মিল আছে -- ক্রন্দনহীন মৃত্যু, আমাদের সক্রিয় কন্যা আর চাকরানি, রাস্তার কাদায় বেপরোয়া ভালোবাসা আর ফালতু অপরাধ ফুঁপিয়ে বেড়াচ্ছে ।
স্তেফান মালার্মে ( ১৮৪২ - ১৮৯৮ ) বাঙালি পাঠকের কাছে তিনি ‘এ রোল অব ডাইস উইল নেভার মিস এ চান্স’ কবিতাটির টাইপসেটিং সাজানোর ও সেকারণে মর্মার্থের বহুত্বের জন্য পরিচিত হলেও, বর্তমানে খুব বেশি পঠিত নন । বলা যায় যে ‘এ রোল অব ডাইস উইল নেভার মিস এ চান্স’ ইউরোপের কবিতার ধারায় বৈপ্লবিক ঘটনা ছিল; ঘুটির চাল ডিগবাজি খেতে-খেতে এঁকে বেঁকে যেভাবে এগিয়ে যেতে পারে সেইভাবে পঙক্তিগুলো সাজিয়েছিলেন মালার্মে ।কবিতার মধ্যে সহজাত শুদ্ধতা ও পরিপূর্ণতা আনার প্রচেষ্টায় ভাষাগত সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করতে না পেরে তিনি প্রায়ই উদ্ভাবনী শব্দ বিন্যাস, জটিল উপমা ও পরীক্ষামূলক মুদ্রণবিদ্যা প্রয়োগ করে কবিতা লিখে পাঠকের বিশ্লেষণ ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। মালার্মের সাহিত্য চর্চায় সারা জীবনের গোঁ ছিল যে, পাঠকরা প্রতীকের অর্থ বুঝুক । সাহিত্য ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক তুষ্টিকে তিনি অবজ্ঞার চোখে দেখতেন । তাঁর বাড়িতে প্রতি মঙ্গলবার সাহিত্যিকদের আড্ডা বসতো, কিন্তু স্কুলে শিক্ষকতা করার দরুণ তাঁর আর্থিক অবস্হা কোনো দিনই ভালো ছিল না ।স্বাভাবিক যে পাঠকদের মনে হয়েছে তাঁর কবিতার ভেতরে ঢোকা যায় না । এখানে তাঁর ‘কবিতার আবির্ভাব’-এর বাংলায়ন দিচ্ছি
দু:খি হয়ে পড়ছিল চাঁদ। কাঁদুনে দেবশিশুরা স্বপ্ন দেখছিল।
শান্ত ও বাষ্পীয় ফুলের তোড়ায় তাদের তীরবাহী আঙুল
যেন তাদের মরণাপন্ন বেহালার তার বাজছিল
আর আকাশ-নীল ফুলের পাপড়িতে গড়িয়ে পড়ছিল স্বচ্ছ অশ্রু।
সে ছিল তোমার প্রথম চুমুর আশীর্বাদ-পাওয়া দিন,
আর আমি আমার স্বপ্নের কাছে শহিদ হলুম,
যা বিষাদের সুগন্ধীর উপর ভর করে বেঁচেছিল,
এমনকি কোনও পরিতাপ বা দূর্ঘটনা ছাড়াই
একটি স্বপ্নকে সেই হৃদয়ের কাছে রেখে গিয়েছে
যে প্রথম স্বপ্নটি তুলেছিল।
এখানে আমি ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম, পাথরে বাঁধানো রাস্তায়
আমার চোখ নাচছিল।
যখন তুমি চুলে সূর্যের উচ্ছাস নিয়ে, রাস্তায় আর রাতের বেলায়
হাসিমুখে আমার কাছে এসেছো,
আর আমি ভাবলুম আলোর টুপি পরা এক পরীকে দেখছি,
যে আমার ছোটোবেলাকার ঘুমে স্বপ্নে দেখা দিত,
আর যার আধখোলা-মুঠো থেকে
সুগন্ধী নক্ষত্রের দলে ঝরে পড়তো তুষারপুঞ্জ
গাছেদের সরু ডালে ।
মহিলা কবি মার্সেলিন দেবোর্দে-ভামো’’র ( ১৭৮৬ - ১৮৪৯ ) জন্ম রনেঁর দুয়া তে। ফরাসি বিপ্লবের কারণে তাঁর বাবার ব্যবসা নষ্ট হয়ে যায় এবং আর্থিক সাহায্যের জন্য মায়ের সঙ্গে গুয়াদালুপ চলে যান; সেখানে তাঁর মা জনডিসে মারা যান আর ষোলো বছর বয়সী মারসেলিঁকে প্যারিসে ফিরে নাটকের দলে যোগ দিয়ে রোজগারের পথ বেছে নিতে হয় । ১৮১৭ সালে নাটকদলের একজন মামুলি অভিনেতা প্রসপার লাশান্তাঁ-ভামোকে বিয়ে করেন । ১৮১৯ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর কাব্যগ্রন্হ ‘এলেজি এবং রোমান্স’ । ১৮২১ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর ক্রীতদাসদের নিয়ে লেখা উপন্যাস ‘অ্যান্টিলেসের সন্ধ্যা’ । তাঁর ‘উদ্বেগ’ কবিতার বাংলায়ন দিচ্ছি এখানে ; ওনার নাম বাঙালি পাঠক শুনেছেন বলে মনে হয় না ; বাঙালি পাঠকের কাছে তিনি সত্যিই অভিশপ্ত :
কি যে আমাকে বিপর্যস্ত করে ? কেনই বা অপেক্ষা করব ?
এই শহরে, বড়ো বেশি বিষাদ ; তা থেকে, প্রচুর অবসর ।
আধুনিক সুখানুভব নামে যা চলছে
প্রতি ঘণ্টার পেষাই থেকে আমাকে সুরক্ষিত করতে পারে না ।
একসময়ে বন্ধুত্ব ছিল, কোনো বইয়ের আকর্ষণ
চেষ্টা ছাড়াই ভরে তুলতো অতিরিক্ত সময় ।
ওহ এই অস্পষ্ট আকাঙ্খার উদ্দেশ্য কি ?
আমি তা এড়িয়ে যাই, কিন্তু উদ্বেগ আমাকে ফিরে দেখতে বলে ।
আনন্দ যদি আমার হর্ষে ধরা না দ্যায়
তাহলে আমি তাকে দুঃখের বিশ্রামেও পাবো না,
তাহলে কোথায়ই বা পাওয়া যায় আমোদপ্রমোদ ?
আর তুমি যে আমাকে যা চাইছি তা দিতে পারো,
তুমি কি আমাকে চিরকালের জন্য ছেড়ে যাবার নির্ণয় নিয়েছ ?
আমাকে বলো, যুক্তিতর্ক, অনিশ্চিত, বিভ্রান্তিকর,
তুমি কি প্রেমের ক্ষমতাকে অনুমতি দেবে আমায় দখল করতে ?
হায়, নামটা শুনলেই আমার হৃদয় কেঁপে ওঠে !
কিন্তু যে ভয় উদ্বুদ্ধ করে তা অমায়িক আর সত্যি ।
যুক্তিতর্ক, তোমার কাছে ফাঁস করার মতন আর কোনো গোপনীয়তা নেই,
আর আমি ভাবি এই নামটি তোমার চেয়ে তাদের কথা বেশি বলেছে !
এবার জানা যাক আগুস্তে ভিলিয়ার্স দ্যলিজলে আদঁ-র ( ১৮৩৮ -৮৯ ) কথা । ব্রিট্যানির এক অভিজাত পরিবারে জন্ম, যদিও তাঁদের আর্থিক অবস্হা ভালো ছিল না আর নির্ভর করতে হতো মায়ের কাকিমা মাদামোয়াজেল দ্য কেরিনুর দান-খয়রাতের ওপর । তার ওপর ভিলিয়ার্সের বাবার গোঁ চাপে যে তিনি মালটায় গিয়ে ফরাসি বিপ্লবের সময়ে লুকোনো গুপ্তধন উদ্ধার করবেন । ফলে তিনি জমি কিনতেন আর গুপ্তধন না পেয়ে বেচতেন । এই করে ফতুর হয়ে যান । ভিলিয়ার্সকেও ডজনখানেক স্কুল পালটাতে হয় । ১৮৫০ এর পর তিনি বেশ কয়েকবার প্যারিসে গিয়ে কাজের খোঁজ করে কিছুই যোগাড় করতে পারেননি । পাকাপাকি প্যারিসে থাকার ব্যবস্হার জন্য তাঁর এক আত্মীয়া মাসিক খরচের ব্যবস্হা করেন । তিনি ল্যাটিন কোয়ার্টারের মদ্যপ কবি-লেখকদের আড্ডায় যোগ দ্যান এবং শার্ল বোদলেয়ারের পরামর্শে এডগার অ্যালান পোর রচনাবলী পড়া আরম্ভ করেন । ১৮৫৯ সালে নিজের টাকায় প্রকাশ করেন ‘প্রথম কবিতাবলী’ । বইটা কোথাও আলোচিত হলো না । উপরন্তু তিনি লুইজি দায়োনে নামে এক বহুবল্লভা যুবতীর সঙ্গে বসবাস আরম্ভ করলেন ; তাঁর পরিবারে সদস্যদের চাপে ১৮৬৪ সালে যুবতীটিকে ছেড়ে গীর্জায় আশ্রয় নিতে হয় । ভিলিয়ার্স অনেক চেষ্টা করেও বিয়ে করার মতন যুবতী পাচ্ছিলেন না ; তিনি থিয়োফিল গতিয়েকে তাঁর মেয়ে এসতেলে সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব দিলে গতিয়ের তাঁকে তাড়িয়ে দিয়ে বলেন যে তিনি ভবঘুরে মাতাল অখ্যাত কবির সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে চান না । অ্যানা আয়ার পাওয়েল নামে বৈভবশালী ইংরাজ যুবতীকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েও প্রত্যাখ্যাত হন । শেষে তিনি এক বেলজিয় ঘোড়ার গাড়ির চালকের অশিক্ষিতা বিধবা স্ত্রী মারি দানতিনের সঙ্গে বসবাস আরম্ভ করেন আর ১৮৮১ সালে তাঁর ছেলে ভিক্তরের জন্ম হয় । কিন্তু কবিস্বীকৃতি, ভেরলেনের বইতে অন্তর্ভুক্ত হবার আগে, তিনি পাননি । এখানে ভিলিয়ার্সের ‘স্বীকৃতি’ কবিতাটির বাংলায়ন :
যবে থেকে আমি শব্দগুলো ভুলে গেছি, যৌবনের
ফুল আর এপ্রিলের টাটকা বাতাস…
আমাকে তোমার ঠোঁট দুটি দাও ; তাদের সুগন্ধি যৌতুক
গাছেদের ফিসফিস কথাবার্তা হয়ে দেখা দেবে !
যবে থেকে আমি গভীর সমুদ্রের দুঃখ হারিয়েছি
মেয়েটির কান্না, তার অস্হির টান, তার মৃত্যুর আলয়…
একটা শব্দেরও শ্বাস ফেলে না ; তা বিষাদ বা আনন্দ
হয়ে উঠবে ঢেউদের কলকল-ধ্বনি !
যবে থেকে আমার আত্মায় অন্ধকারের ফুল
আত্মমগ্ন, আর পুরোনো সূর্ষেরা উড়াল নেয়…
প্রিয়তমা আমাকে তোমার মলিন বুকে লুকিয়ে নাও,
আর তা হয়ে উঠবে রাতের প্রশান্তি !
কিন্তু অভিশপ্ত কবিদের তালিকায় তাঁর গুরু শার্ল বোদলেয়ার, কোঁতেদ্য লুতিয়ামোঁ (Comte de Lautréamont ) , অ্যালিস দ্য শমবিয়ে ( Alice de Chambrier ), আঁতোনা আতো ( Antonin Artaud ), জঁ-ফিয়ে দ্যুফে ( Jean-Pierre Duprey ) প্রমুখকে যোগ করেন পরবর্তীকালের আলোচকরা ; বস্তুত পল ভেরলেনই ছিলেন সবচেয়ে বেশি অভিশপ্ত। এই কবিরা তাঁদের কবিতার জন্য অভিশপ্ত নন ; তাঁদের জীবনের দুঃখ, বিষাদ, আর্থিক দৈন্য, পরাজয়বোধ, অবহেলা, মাদকে আসক্তি, যৌনরোগ ইত্যাদির কারণে তাঁদের মনে করা হয়েছে ‘অভিশপ্ত’। তাঁর মৃত্যুর পর Fin de siècle বা শতাব্দী শেষের কবিদের অন্যতম মনে করে হয় পল ভেরলেনকে।
প্রথমে পড়া যাক শার্ল বোদলেয়ারের গদ্য কবিতার বই ‘বিষণ্ণ প্যারিস’ এর একটি রচনা :
আমাকে তোমার চুলের দীর্ঘ, দীর্ঘ সুগন্ধ নিতে দাও, ঝর্ণার জলে পিপাসার্তের মতন আমার মুখকে সম্পূর্ণ ডুবে জেতে দাও, সুবাসিত রুমালের মতন হাতে নিয়ে খেলতে দাও, বাতাসে স্মৃতিকে উড়িয়ে দিতে দাও ।
আমি যাকিছু দেখি তা তুমি যদি জানতে -- যাকিছু আমি অনুভব করি -- তোমার চুলে যাকিছু আমি শুনতে পাই ! অন্য লোকেদের আত্মা সঙ্গীতের প্রভাবে যেমন ভ্রমণে বেরোয় তেমনই আমার আত্মা ভ্রমণে বেরোয় এই সুগন্ধে।তোমার চুলে রয়েছে একটি পুরো স্বপ্ন, পাল আর মাস্তুলসহ ; তাতে রয়েছে বিশাল সমুদ্র, যেখানে অগুনতি মৌসুমীবায়ু আমাকে বয়ে নিয়ে যায় মোহিনী আবহাওয়ায়, যেখানে আকাশ আরও নীল আর আরও নিগূঢ়, যেখানে বাতাবরণকে সুগন্ধিত করে তুলেছে ফল, পাতা, আর মানুষের ত্বক।
তোমার চুলের সাগরে, আমি দেখতে পাই দুঃখী গানে সমাহিত বন্দর, সব কয়টি দেশের কর্মঠ মানুষ সেখানে, যতো রকম হতে পারে ততো ধরণের জাহাজ, বিশাল আকাশের অলস শাশ্বত তাপের পৃষ্ঠভূমিতে তাদের স্হাপত্য দিয়ে দিগন্তকে তনূকৃত ও জটিল করে তুলেছে।
তোমার চুলের সোহাগস্পর্শে আমি কাউচে শুয়ে কাটানো দীর্ঘ ধীরুজ সময়কে ফিরে পাই, সুন্দর জাহাজের একটি ঘরে, বন্দরের অনির্ণেয় ঢেউয়ের দ্বারা ক্রমান্বয়ে দোল খাওয়া, তাজা জলের জালা আর ফুলের টবের মাঝে ।
আগুনের পাশে রাখা কম্বলের মতন তোমার চুলে, আমি আফিম আর চিনির সঙ্গে মেশানো তামাকের শ্বাস নিই ; তোমার চুলের রাত্রিতে, আমি দেখতে পাই অসীম ক্রান্তিবৃত্তের নীলাভ ঔজ্বল্য; তোমার চুলের ঢালের কিনারায়, আমি আলকাৎরা, মৃগনাভি আর নারিকেল তেলের গন্ধে মাতাল হয়ে যেতে থেকি ।
আমাকে একটু-একটু করে খেয়ে ফেলতে থাকে তোমার তন্দ্রাতুর কালো বিনুনি । যখন তোমার স্হিতিস্হাপক, দ্রোহী চুল আমি চিবোতে থাকি, আমার মনে হয় আমি স্মৃতিগুলো খেয়ে ফেলছি।
কঁতে দ্য লুতিয়ামোর ( ১৮৪৬ - ১৮৭০ ) প্রকৃত নাম ইসিদোরে লুসিয়েন দুকাস, জন্মেছিলেন উরুগুয়েতে । তাঁর জন্মের পরেই মা মারা যান ; তখন আর্জেনটিনা আর উরুগুয়ের যুদ্ধ চলছে । তাঁর বাবা, যিনি ফরাসিভাষী ছিলেন, তাঁকে তেরো বছর বয়সে প্যারিসে পাঠিয়ে দ্যান স্কুল শিক্ষার জন্য । সতেরো বছর বয়সে উচ্চ বিদ্যালয়ে তিনি দাঁতে, মিলটন, বোদলেয়ার এবং রাসিনে মুখস্হ বলতে পারতেন বলে শিক্ষকদের প্রিয় ছিলেন । কিন্তু নির্ণয় নেন যে তিনি নিজে ‘নিষ্ঠুরতার আনন্দবোধ’ নিয়ে কবিতা লিখবেন । ‘মালদোরোরের গান’ নামে তিনি একটি কাব্যোপন্যাস লেখেন, ১৯৬৮ থেকে ১৯৬৯ সালের মাঝে, তাঁর এই নির্ণয়কে রূপ দেবার জন্য । নায়কের নাম মালদোরোর । বইটি ছয় পর্বে আর ষাটটি কবিতাংশে বিভাজিত । ডাডাবাদীরা, পরাবাস্তববাদীরা, বিশেষ করে সালভাদোর দালি, তাঁর এই বইটির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন । বইটির বহু দৃশ্যের এচিং করেছিলেন দালি । আমি বইটি থেকে একটি কবিতাংশ তুলে দিচ্ছি:
আমি নোংরা । আমার সারা শরীরে উকুন । শুয়োররা, যখন আমার দিকে তাকায়, বমি করে। আমার চামড়া কুষ্ঠরোগের মামড়ি আর আঁশে ছয়লাপ, আর তার ওপরে হলুদ রঙের পুঁজ । আমার বাঁদিকের বগলে এক ব্যাঙ পরিবার বসবাস আরম্ভ করেছে, আর, তাদের কোনো একটা নড়াচড়া করলে, কাতুকুতু দ্যায় । মনে রাখতে হয় যাতে বাইরে বেরিয়ে মুখ দিয়ে কান আঁচড়াতে না আরম্ভ করে ; তাহলে সেটা মগজে ঢুকে যাবে । আমার ডানদিকের বগলে রয়েছে একটা গিরগিটি যে সব সময়ে ওদের তাড়া করে যাতে খাবার না জোটায় মারা যায় : সবাইকে তো বাঁচতে হবে । আমার পোঁদের ভেতরে একটা কাঁকড়া ঢুকে গেছে ; আমার কুঁড়েমিতে উৎসাহিত হয়ে, ঢোকার পথটা নিজের দাড়া দিয়ে পাহারা দ্যায় আর আমাকে দ্যায় অসহ্য যন্ত্রণা ।
অ্যালিস দ্য শমবিয়ে ( ১৮৬১ - ১৮৮২ ) একুশ বছর বয়সে কোমায় আক্রান্ত হয়ে মারা যান, তার কিছুকাল আগেই তিনি লিখেছিলেন ‘ঘুমন্ত সুন্দরী’ । তাঁর অধিকাংশ বই প্রকাশিত হয়েছে তাঁর মৃত্যুর পর । এখানে তাঁর ‘পলাতক’ কবিতাটির বাংলায়ন :
আমরা সবাই আগন্তুক আর পৃথিবী হয়ে চলে যাই
খেলার সময়ে উধাও আলোর নৌকোর মতো
হালকা হাওয়ায় চুপিচুপি চুমুর আড়ালে,
আর নীল দিগন্ত ক্রমশ বিলীন হয়ে যায় ;
উড়ালের সময়ে যদি হলরেখার খাত গড়তে পারে তাহলে আনন্দিত
সে চলে যাবার পরে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করো ;
যে পথ সে দ্রুত যাত্রায় খুঁজতে চেয়েছিল
কোনো ঘুর্ণিঝড় তাকে মুছে দিতে পারে না;
আনন্দিত, যদি অদৃষ্ট আমাদের টেনে বের করে আনে
আমরা তবুও হৃদয় হয়ে বাঁচি যেখানে থেকেছি চিরকাল,
সুদূর সমুদ্রতীর পর্যন্ত যে হৃদয় আমাদের অনুসরণ করে
তাহলে এখানে এক মৃত মানুষের সমাধিকে কী বলা হবে ?
আঁতোনা জোসেফ মারি আতো ( ১৮৯৬ - ১৯৪৮ ), যিনি আঁতোনা আতো নামে অধিক পরিচিত, ছিলেন কবি, নাট্যকার, প্রাবন্ধিক, অভিনেতা, নাট্য পরিচালক এবং ইউরোপীয় আভাঁগার্দ আন্দোলনের পুরুষদের অন্যতম । ‘থিয়েটার অব ক্রুয়েলটি’ তত্বটির জন্য তিনি অধিকতর পরিচিত । যদিও তাঁর জন্ম ফ্রান্সের মার্সাইতে, তাঁর বাবা-মা ছিলেন গ্রিক । জাহাজের মালিক ছিলেন তাঁর বাবা । তাঁর মায়ের নয়টি বাচ্চা হয়েছিল, চারটি মৃত অবস্হায় জন্মায় আর দুটি শৈশবেই মারা যায় । পাঁচ বছর বয়সে আতো আক্রান্ত হন মেনেনজাইটিসে, যার দরুন কোমাটোজে ছিলেন কিছুকাল এবং বিভিন্ন স্যানাটোরিয়ামে চিকিৎসার জন্য পাঁচ বছর ভর্তি ছিলেন । ১৯১৬ সালে তাঁকে বাধ্যতামূলক সেনাবাহিনিতে যোগ দিতে হয়েছিল কিন্তু মানসিক অস্হিরতার কারণে ছাঁটাই হন । দীর্ঘ রোগভোগের দরুণ তাঁকে ল্যডানডাম ওষুধ ( অ্যালকোহলে গোলা আফিম ) নিতে হতো আর সেখান থেকেই তাঁর আফিমের নেশা ।সাতাশ বছর বয়সে তিনি এক গোছা কবিতা ‘নতুন ফরাসি রিভিউ’ ( Nouvelle Revue Française ) পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠান ; তা প্রত্যাখ্যাত হলেও সম্পাদক তাঁর কবিতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে চিঠি লেখেন এবং বেশ কিছু সময় তাঁদের মধ্যে চিঠির আদান-প্রদান হয় । এখানে তাঁর কয়েকটা কবিতার বাংলায়ন দিলুম, কেননা তাঁর কবিতার বই সহজে পাওয়া যায় না :
নিরংশু কবি
নিরংশু কবি, একটি তরুণীর বুক
তোমাকে হানা দিয়ে বেড়ায়,
তিক্ত কবি, জীবন ফেনিয়ে ওঠে
আর জীবন পুড়তে থাকে,
আর আকাশ নিজেকে বৃষ্টিতে শুষে নেয়,
জীবনের হৃদয়ে নখের আঁচড় কাটে তোমার কলম ।
অরণ্য, বনানী, তোমার চোখ দিয়ে প্রাণবন্ত
অজস্র ছেঁড়া পালকের ওপরে ;
ঝড় দিয়ে বাঁধা চুলে কবি চাপেন ঘোড়ায়, কুকুরের ওপরে ।
চোখ থেকে ধোঁয়া বেরোয়, জিভ নড়তে থাকে
আমাদের সংবেদনে স্বর্গ উথালপাথাল ঘটায়
মায়ের নীল দুধের মতন ;
নারীরা, ভিনিগারের কর্কশ হৃদয়,
তোমাদের মুখগহ্বর থেকে আমি ঝুলে থাকি ।
আমার টাকাকড়ি নেই
আমার টাকাকড়ি নেই কিন্তু
আমি
আঁতোনা আতো
আর আমি ধনী হতে পারি
ব্যাপকভাবে আর এক্ষুনি ধনী হতে পারি
যদি আমি তার জন্য প্রয়াস করতুম ।
সমস্যা হলো আমি চিরকাল টাকাকড়িকে,
ধনদৌলতকে, বৈভবকে ঘৃণা করেছি ।
কালো বাগান
এই কালো পাপড়িগুলো ভারতের আকাশের ঘুর্ণাবর্তকে ঘোরাও।
ছায়ারা পৃথিবীকে ঢেকে ফেলেছে যা আমাদের সহ্য করে ।
তোমার নক্ষত্রদের মাঝে চাষের জমিতে পথ খুলে দাও ।
আমাদের আলোকিত করো, নিয়ে চলো তোমার নিমন্ত্রণকর্তার কাছে,
চাঁদির সৈন্যবাহিনী, নশ্বর গতিপথে
আমরা রাতের কেন্দ্রের দিকে যেতে চেষ্টা করি ।
আমি কে
আমি কে ?
আমি কোথা থেকে এসেছি ?
আমি আঁতোনা আতো
আর আমি একথা বলছি
কেননা আমি জানি তা কেমন করে বলতে হয়
তাৎক্ষণিকভাবে
তুমি আমার বর্তমান শরীরকে দেখবে
ফেটে গিয়ে বহু টুকরো হয়ে গেছে
আর তাকে আবার গড়ে ফেলবে
দশ হাজার কুখ্যাত পরিপ্রেক্ষিতে
এক নতুন শরীর
তখন তুমি আমাকে
কখনও ভুলতে পারবে না ।
স্নায়ু ছন্দ
একজন অভিনেতাকে দেখা হয় যেন স্ফটিকের ভেতর দিয়ে ।
মঞ্চের ওপরে অনুপ্রেরণা ।
সাহিত্যকে বেশি প্রবেশ করতে দেয়া উচিত নয় ।
আমি আত্মার ঘড়ি ধরে কাজ করা ছাড়া আর কোনো চেষ্টা করিনি,
আমি কেবল নিষ্ফল সমন্বয়ের যন্ত্রণাকে লিপ্যন্তর করেছি ।
আমি একজন সম্পূর্ণ রসাতল ।
যারা ভেবেছিল আমি সমগ্র যন্ত্রণার যোগ্য, এক সুন্দর যন্ত্রণা,
এক ঘন আর মাংসল পীড়া, এমন এক পীড়া যা বিভিন্ন বস্তুর মিশ্রণ,
বুদবুদ-ভরা একটি নিষ্পেশিত ক্ষমতা
ঝুলিয়ে রাখা বিন্দু নয় — আর তবু অস্হির, উপড়ে-তোলা স্পন্দনের সাহায্যে
যা আমার ক্ষমতা আর রসাতলের দ্বন্দ্ব থেকে আসে
শেষতমের উৎসার দেয় ( ক্ষমতার তেজের দ্বন্দ্বের মাপ বেশি ),
আর কোনও কিছু বাকি থাকে না বিশাল রসাতলগুলো ছাড়া,
স্হবিরতা, শীতলতা–
সংক্ষেপে, যারা আমাকে অত্যধিক জীবনের অধিকারী মনে করেছিল
আত্মপতনের আগে আমার সম্পর্কে ভেবেছিল,
যারা মনে করেছিল আমি যন্ত্রণাদায়ক আওয়াজের হাতে নির্যাতিত,
আমি এক হিংস্র অন্ধকারে লড়াই করেছি
তারা সবাই মানুষের ছায়ায় হারিয়ে গেছে ।
ঘুমের ঘোরে, আমার পুরো পায়ে স্নায়ুগুলো প্রসারিত হয়েছে ।
ঘুম এসেছে বিশ্বাসের বদল থেকে, চাপ কমেছে,
অসম্ভাব্যতা আমার পায়ের আঙুলে জুতো-পরা পা ফেলেছে ।
মনে রাখা দরকার যে সমগ্র বুদ্ধিমত্তা কেবল এক বিশাল অনিশ্চিত ঘটনা,
আর যে কেউ তা খুইয়ে ফেলতে পারে, পাগল বা মৃতের মতন নয়,
বরং জীবিত মানুষের মতন, যে বেঁচে আছে
আর যে অনুভব করে জীবনের আকর্ষণ আর তার অনুপ্রেরণা
তার ওপর কাজ করে চলেছে ।
বুদ্ধিমত্তার সুড়সুড়ি আর এই প্রতিযোগী পক্ষের আকস্মিক প্রতিবর্তন ।
বুদ্ধিমত্তার মাঝপথে শব্দেরা ।
চিন্তার প্রতিবর্তন প্রক্রিয়ার সম্ভাবনা একজনের চিন্তাকে হঠাৎ নোংরামিতে পালটে দ্যায় ।
এই সংলাপটি চিন্তার অন্তর্গত ।
ভেতরে ঢুকিয়ে নেয়া, সবকিছু ভেঙে ফেলা ।
আর হঠাৎ আগ্নেয়গিরিতে এই পাতলা জলের স্রোত, মনের সরু, আস্তে-আস্তে পতন ।
আরেকবার নিজেকে ভয়ঙ্কর অভিঘাতের মুখোমুখি আবিষ্কার করা, অবাস্তবের দ্বারা নিরসিত, নিজের একটা কোনে, বাস্তব জগতের কয়েকটা টুকরো-টাকরা ।
আমিই একমাত্র মানুষ যে এর পরিমাপ করতে পারি ।
১৯৫০ সালে, কুড়ি বছর বয়সে, জাঁ ফিয়ে দুফের (১৯৩০ - ১৯৫৯ ) প্রথম কবিতার বই ‘দ্বিতীয়ের পেছনে’র পাণ্ডুলিপি পড়ে আঁদ্রে ব্রেতঁ তাঁর প্রশংসা করেছিলেন । এক বছর পরে তিনি কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়ে ভাস্কর্যে আগ্রহী হন, আর পাঁচের দশকের পুরো সময় লোহা আর সিমেন্টের কাজ করেন, সেই সঙ্গে চারকোল ও কালির কাজও করেন । ১৯৫৯ সালে ব্যক্তিগত দ্রোহ প্রকাশ করার জন্য আর্ক দ্য ত্রয়েম্ফে অজানা সেনাদের শিখায় পেচ্ছাপ করার সময়ে ধরা পড়েন আর জনগণের পিটুনি খেয়ে প্রথমে কারাগারে আর তারপর পাগলাগারদে যেতে হয় । ছাড়া পেয়ে আবার কবিতা লেখা আরম্ভ করেন এবং ‘শেষ ও উপায়’ কাব্যগ্রন্হের পাণ্ডুলিপি স্ত্রীর হাতে দিয়ে নির্দেশ দ্যান তা ব্রেতঁকে ডাকে পাঠিয়ে দিতে । বাড়ি ফিরে স্ত্রী জ্যাকলাঁ দেখতে পান যে ছবি আঁকার ঘরের কড়িকাঠ থেকে ঝুলে জাঁ ফিয়ে দুফে আত্মহত্যা করেছেন । কাব্যগ্রন্হটি থেকে ‘সম্পূর্ণ’ শিরোনামের গদ্য কবিতাটির বাংলায়ন :
জগতসংসার সম্পূর্ণ । কে সেই লোক যে রাতকে প্রতিবার একই ফাঁদে ফ্যালে ? আমি, যদি বলা হয়, কাউকেই চিনি না আর যে আকাশ আমার ওপর মনের ঝাল মেটায়, ওর বড়ো ইঁদুরের হাত আমাকে কখনও, কখনও দেখায়নি ।
কেউ একজন দরোজাটা খুললো : ভেতরে ছিল না কেউ, ভেতরে তার ছিল হাড় আর হাড়, আর আমি প্রতিজ্ঞা করে সবাইকে জানিয়েছি যে আমি জ্যান্ত ওর চামড়া ছাড়িয়ে নেবো ।
জগতসংসার ভয়ঙ্করভাবে সম্পূর্ণ ছিল আর জিনিসপত্রের টানাটানি চলছিল । কেউ একজন দুঃস্বপ্নকে সাজিয়ে রাক্ষসদের আলোকিত করছিল আর তাকে বলা হচ্ছিল বর্তমান, এখন…
এই বর্তমানগুলো আমাদের বহু সংগ্রহকে সমৃদ্ধ করেছিল, আমি থেকে আমিতে, আমার থেকে আমার সঙ্গে আর অন্য অনেকের সঙ্গে, আর আমার সঙ্গে অন্য অনেকের...কিন্তু অনেকসময়ে সবচেয়ে বিচক্ষণ ভাগাভাগিও আমাদের আলাদা করতে পারে, কিন্তু মাথা কখনও, আর আমি বলতে চাই কখনও, কাঁধের ওপরে স্হিতিশীল থাকেনি ।
দুই
‘অভিশপ্ত বুদ্ধিজীবীদের’ কালখণ্ডে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন জাগে যে পল ভেরলেন চল্লিশ বছর বয়সে কয়েকজন কবিকে ‘অভিশপ্ত কবি’ চিহ্ণিত করে একটা বই লিখলেন কেন ? তিনি কি আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিলেন, নাকি নিজেকে দেখতে চাইছিলেন সেই কবিদের সারিতে যাঁদের তিনি গুরুত্বপূর্ণ কবি মনে করলেও তখনকার ‘বুর্জোয়া পাঠক’ কোনও পাত্তা দিতেন না । চল্লিশ বছর বয়সে র্যাঁবোকে খুনের চেষ্টার দায়ে জেল খেটে ফিরেছেন, একজনকে ( অনেকের মতে নিজের মা-কে ) মারধর করার কারণে আবার জেলে গিয়েছিলেন, রোমান ক্যাথলিক হিসাবে দীক্ষা নিয়েছেন, তবু তাঁর কেন মনে হয়েছিল তাঁর মতনই কয়েকজন কবি অভিশপ্ত ? সাধারণ পাঠকের কাছে তাঁরা ছিলেন অখ্যাত, সমাজ তাঁদের প্রতি উদাসীন ছিল কেননা তাঁদের কবিতা তারা বুঝে উঠতে পারছিল না । কেবল রসপণ্ডিতরা তাঁদের কবিতায় আগ্রহী ছিলেন আর সেকারণে তাঁদের জীবন দুর্দশাপূর্ণ ছিল । উপেক্ষার, এমনকি ‘বুর্জোয়া অশিক্ষিতদের দ্বারা’ পদদলিত হবার চর্চিত বোধ, হয়তো ছিল প্রথম পর্বের আভাঁ গার্দ লেখক-কবিদের ধ্রুপদি দাবি।ফরাসিদেশের কবি-চিত্রকরদের মাঝে আত্মক্ষয়ের গৌরব প্রশংসনীয় ছিল তাঁদের নিজেদের গণ্ডিতে ।
অভিশাপটি একই সঙ্গে যতোটা নৈতিক ও আত্মিক মনে করেছিলেন ভেরলেন, ততোটাই সামাজিক, যে মানসিকতা থেকে এই বোধের সূত্রপাত যে ‘সত্যকার শিল্পীকে’ প্রতিভার চাপ সহ্য করে ক্লেশ ও নিদারুণ-যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় । চল্লিশ বছর বয়সে ভেরলেন মাতলামি, স্ত্রী ও মাকে মারধর করে, বাচ্চাকে যাতনা দিয়ে, সিফিলিসে ভুগে, বস্তিতে জীবন কাটিয়ে, ভিক্ষাবৃত্তি করে, জীবনের মর্মভেদী যন্ত্রণাদায়ক অভিজ্ঞতাগুলোর সঙ্গে অতিপরিচিত হয়ে গিয়েছিলেন এবং কবিদের ক্ষেত্রে ‘অভিশাপ’ যে কেবল সমাজের দেয়া নয়, তাঁরা নিজেরাও এমন সমস্ত কাজকর্ম করেছেন যে প্রকৃতি তাঁদের জীবনে বিপদ ডেকে এনেছে, তাঁদের দেহ ও অন্তরজগতকে ক্ষইয়ে দিয়েছে, তা টের পেয়েছিলেন তিনি ।
পল ভেরলেনের কাছে ‘অভিশপ্ত কবির’ প্রধান দৃষ্টান্ত ছিলেন শার্ল বোদলেয়ার ( ১৮২১ - ১৮৬৭ ) যাঁর ‘পাপের ফুল’ ( Les fleurs du mal ), ১৮৫৭ সালে প্রকাশিত, ছিল উনিশ শতকের সবচেয়ে বিখ্যাত কাব্যগ্রন্হ এবং পৃথিবীর সাহিত্যে অতুলনীয় । বইটির কবিতাগুলোয় ছিল সৌন্দর্যের সঙ্গে ইতরতার বৈপ্লবিক মিশ্রণ, তাতে প্রতিফলিত হয়েছিল চরম আধ্যাত্মিকতা যার জন্য আধুনিক যুগ বহুকাল অপেক্ষা করছিল, যা একই সঙ্গে ছিল স্বর্গে ঝড়-তোলা ও নাছোড়বান্দাভাবে নারকীয় । মর্ত্যে নরকভোগের অভিজ্ঞতা শার্ল বোদলেয়ারের ছিল, এবং তার অধিকাংশ তাঁর নিজের গড়া নরক । লাতিন কোয়ার্টার থেকে তুলে এনেছিলেন এক শ্যামলী বেশ্যাকে, আর তার থেকে প্রেমের পাশাপাশি পেয়েছিলেন সিফিলিস । তেত্রিশ বছর বয়সে মাকে বোদলেয়ার লিখেছিলেন, “আমি প্রথম থেকেই জঘন্য।” অথচ উত্তরাধিকারসূত্রে যা টাকাকড়ি পেয়েছিলেন, তিনি সারাজীবন আরামে জীবন কাটাতে পারতেন । আঁতোনা আতোর মতন বোদলেয়ারও লডানডাম ( মদে মেশানো আফিম ) মাদকের নেশা ছাড়তে পারেননি । যে লোক নিজেকে অভিশপ্ত মনে করে, সে তার কারণ খোঁজে । বোদলেয়ারে পাওয়া যায় যিশুখ্রিস্টের উপহাস । ‘সেইন্ট পিটারের অস্বীকৃতি’ কবিতায় বোদলেয়ার বলছেন:
আহ ! যিশু, অলিভের বাগানকে মনে করো !
তোমার সারল্যে তুমি হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা করেছিলে তার কাছে
যে স্বর্গে রয়েছে সে হাসছিল পেরেকের শব্দে
যেগুলো নীচ জল্লাদেরা তোমার মাংসে পুঁতে দিচ্ছিল ।
বিশোধক যন্ত্রণাবোধের ধারণাকে বোদলেয়ার দিয়েছেন এক বিশেষ উতরাই, যা টেনেছিল পল ভেরলেনকে । ভেরলেন জানতেন যে বোদলেয়ারের নায়ক ছিলেন এডগার অ্যালান পো, যিনি, বোদলেয়ারের মতে, অত্যধিক মদ খাবার কারণে মারা যান, ‘অভিশপ্ত কবি’র সৃষ্টিক্ষমতা ও আত্মধ্বংসের ক্ষমতা দুটিই ছিল অ্যালান পোর অহংকার । বোদলেয়ারের চরস আর আফিমের নেশা ছিল যা তিনি ক্ষতিকর মনে করেও ছাড়তে পারেননি ; ‘অভিশপ্ত কবির’ যদি মনে হয় মাদক তাঁর চেতনাকে উন্নীত করছে, তাহলে তার ক্ষতিকর প্রভাবকে প্রতিভার দাম চোকানো হিসেবে তিনি মান্যতা দেবেন । এডগার অ্যালান পো, শার্ল বোদলেয়ার ও পল ভেরলেনের মাতাল-অবস্হায়-থাকা হয়ে উঠেছিল এক ধরণের আধ্যাত্মিক নিয়মনিষ্ঠা ।
পল ভেরলেন মধ্যস্হ, মীমাংসক, শান্তিস্হাপকের বেদিতে বসিয়েছিলেন শার্ল বোদলেয়ারকে । ভেরলেন লিখেছেন, “আমার কাব্যিক অনুভূতিকে, এবং আমার গভীরে যা রয়েছে, তাকে জাগিয়ে তুলেছিলেন বোদলেয়র।” একুশ বছর বয়সে ভেরলেন লিখেছিলেন, “শার্ল বোদলেয়ার উপস্হিত করতে পেরেছেন সংবেদনশীল মানুষকে, এবং তিনি তাকে উপস্হাপন করেন একটি আদর্শ হিসাবে, বা বলা যায়, নায়ক হিসাবে ।” ভেরলেন আরও বললেন যে, শার্ল বোদলেয়ার “একজন দ্রষ্টা ; তাঁর রয়েছে তীক্ষ্ণ, স্পন্দমান সংবেদন, একটি যন্ত্রণাময় নিগূঢ় মন, তাঁর ধীশক্তি তামাকে প্লাবিত, তাঁর রক্ত বিশুদ্ধ সুরাসারে প্রজ্বলন্ত ।” যেহেতু অভিশপ্ত, তাই আশীর্বাদপূত ।
বোদলেয়ারকে নায়কের বেদিতে বসিয়ে তাঁর জীবনযাত্রা অনুকরণের প্রয়াস করলেন পল ভেরলেন । মদে চোবানো অফিমের বদলে তিনি আসক্ত হলেন আবসাঁথে । আবসাঁথে আর কিছু মেশাতে হয় না, সরাসরি পান করতে হয় এবং গাঢ় নেশা হয় । বন্ধুরা নিষেধ করলে ভেরলেন তাঁদের সঙ্গে তরোয়াল বের করে মুখোমুখি হতেন । ভেরলেনের হাতে দেশলাই দেখলে তাঁর বন্ধুরা ভয় পেতেন । স্ত্রীর চুল সুন্দর বলে তাতে আগুন ধরাবার চেষ্টা করেছিলেন । যখন ‘অভিশপ্ত কবি’ ভেরলেন লিখছেন, এবং দুঃখদুর্দশায় জীবন কাটাচ্ছেন, তিনি জানতেন না যে তাঁর বেশ কিছু কবিতা সাধারণ পাঠকের কাছে পৌঁছেচে । কিন্তু তাঁর মনের মধ্যে ক্ষোভ মৃত্যু পর্যন্ত ছিল যে তাঁকে আর তাঁর কবিতাকে কেউ ঠিকমতন বুঝতে পারেনি ; তাঁর মনে হতো একজন কবির কাব্যিক প্রতিভার কারণে যে আবেগের ঝড় তাকে পুষতে হয় তা লোকে টের পায় না ; প্রথানুসরণ সত্যকার শিল্পের শ্বাসরোধ করে, তাই সীমালঙ্ঘন জরুরি হয়ে ওঠে মৌলিকতাকে আয়ত্ব করার জন্য, নয়তো কবিতা হয়ে উঠবে আহরিত ; জীবনকে আত্মাহীন হলে চলবে না, তাকে হতে হবে অকৃত্রিম ও বিশ্বাসযোগ্য ।
বোদলেয়ার, ভেরলেন, র্যাঁবোর সময়ে, ইউরোপেও, অভিশপ্ত কবির যুক্তি খাটতো, কিন্তু এখন সেগুলো কিংবদন্তি মনে হয় । ইউরোপ-আমেরিকায় নৈতিক বিপথগামীতার নতুন সংজ্ঞা বাজারের চালচলনের সঙ্গে বদলাতে থাকে । এমনকি ভারতেও বোদলেয়ার বা ভেরলেনের মতন অভিশপ্ত কবির যুগ শামসের আনোয়ার ও ফালগুনী রায়ের সঙ্গে শেষ হয়ে গেছে । এখন এসেছে অভিশপ্ত বুদ্ধিজীবির কালখণ্ডে । যাতে উপেক্ষার অভিশাপে না পড়তে হয় তাই কবি-লেখকরা এখন শাসকদলের ছত্রছায়ায় আশ্রয় নিতে চান । পশ্চিমবঙ্গে সিপিএমের সময়ে যাঁরা লাল ঝাণ্ডা নিয়ে মিছিল করতেন তাঁরা অনেকেই তৃণমূলের মন্ত্রীর পাশে বসে ফোটো তোলাতে কার্পণ্য করেন না। রাষ্ট্র এখন এমনই বেপরোয়া যে কাকে কোন অভিযোগে জেলে পুরে দেবে তার নিশ্চয়তা নেই । কেবল রাষ্ট্র নয়, বিভিন্ন গোষ্ঠীও বুদ্ধিজীবিদের খুন করতে ভয় পায় না । নকশাল নামে একদা বহু বুদ্ধিজীবি লোপাট হয়ে ছিলেন ; এখন ‘শহুরে নকশাল’ নামে কয়েকজনকে জেলে পোরা হয়েছে । ধর্মবাদীদের হাতে খুন হয়েছেন কর্ণাটক আর মহারাষ্ট্রের কয়েকজন বুদ্ধিজীবি ।
সমাজের যাঁরা নৈতিকতার জ্যাঠামশায়, তাঁরা সাহিত্যিকদের আত্মধ্বংসে সমাজেরই পচন দেখতে পান । বোদলেয়ার, ভেরলেন, র্যাঁবোর সময়ে ইউরোপের সমাজে ও রাজনীতিতে বিপুল রদবদল ঘটছিল, যা আমরা দেড়শো বছর পরে ভারতেও প্রত্যক্ষ করছি । এখন ইউরোপ আমেরিকায় ধর্মহীনতা ও যৌন-যথেচ্ছাচারকে অধঃপতন মনে করা হয় না, যা ভেরলেনের সময়ে করা হতো । ১৮৫৭ সালে বোদলেয়ারের ছয়টি কবিতাকে নিষিদ্ধ করার ঘটনা এখন ভারতীয় মাপকাঠিতেও হাস্যকর মনে হয় । ভেরলেনেরও মনে হয়ে থাকবে, যে, কবিতাগুলো কোন যুক্তিতে জনগণের নৈতিকবোধে আঘাত হেনেছে, যখন কিনা জনগণ নিজেরাই জীবনে বহু ঘটনা চেপে যায় । কলকাতায় কৃত্তিবাস গোষ্ঠীর বেশ কয়েকজন কবি অবিনাশ কবিরাজ লেনে যেতেন অথচ আত্মজীবনী লেখার সময়ে তা চেপে গেছেন । বোদলেয়ারের ছয়টা কবিতা থেকে নিষেধ তোলা হয় ১৯৪৯ সালে । অথচ তার কয়েক বছর পরেই দেখা দিয়েছিলেন আমেরিকার বিট জেনারেশনের কবিরা ; অ্যালেন গিন্সবার্গের ‘হাউল’ ঝড় তুলেছে । প্যারিস থেকে তার আগে ১৯৩৪ সালে প্রকাশিত হয়েছিল হেনরি মিলারের ‘ট্রপিক অব ক্যানসার’ । অতিযৌনতা, ভিক্ষাবৃত্তি, নেশা ইত্যাদি সত্বেও হেনরি মিলার নিজেকে অভিশপ্ত মনে করেননি ।
বোদলেয়ারের নিষিদ্ধ কবিতা ‘লিথি’, বুদ্ধদেব বসুর অনুবাদে :
উঠে আয় আমার বুকে, নিষ্ঠুর নিশ্চেতনা
সোহাগী ব্যাঘ্রী আমার, মদালস জন্তু ওরে
প্রগাঢ় কুন্তলে তোর ডুবিয়ে, ঘণ্টা ভরে,
চঞ্চল আঙুল আমার -- হয়ে যাই অন্যমনা ।
ঘাঘরায় গন্ধ ঝরে, ঝিমঝিম ছড়ায় মনে
সেখানে কবর খোঁড়ে আমার এ-খিন্ন মাথা,
মৃত সব প্রণয় আমার, বাসি এক মালায় গাঁথা
নিঃশ্বাস পূর্ণ করে কি মধুর আস্বাদনে !
ঘুমোতে চাই যে আমি যে-ঘুমে ফুরোয় বাঁচা,
মরণের মতোই কোমল তন্দ্রায় অস্তগামী
ক্ষমাহীন লক্ষ চুমোয় তনু তোর ঢাকবো আমি--
উজ্বল তামার মতো ও-তনু, নতুন, কাঁচা ।
শুধু তোর শয়ন ‘পরে আমার এ-কান্না ঘুমোয়,
খোলা ঐ খন্দে ডুবে কিছু বা শান্তি লোটে ;
বলীয়ান বিস্মরণে ভরা তোর দীপ্ত ঠোঁটে
অবিকল লিথির ধারা বয়ে যায় চুমোয় চুমোয় ।
নিয়তির চাকায় বাঁধা, নিরুপায় বাধ্য আমি,
নিয়তির শাপেই গাঁথি ইদানিং ফুল্লমালা ;
বাসনা তীব্র যতো, যাতনার বাড়ায় জ্বালা--
সবিনয় হায়রে শহিদ নির্মল নিরয়গামী !
এ-কঠিন তিক্ততারে ডোবাতে, করবো শোষণ
ধুতুরার নেশায় ভরা গরলের তীব্র ফোঁটায়
ঐ তোর মোহন স্তনের আগুয়ান দৃপ্ত বোঁটায়--
কোনোদিন অন্তরে যার হৃদয়ের হয়নি পোষণ ।
সমালোচকদের স্বীকৃতি পাচ্ছিলেন না বোদলেয়ার, ফলে যাত্রা আরম্ভ করেছিলেন আত্মক্ষয়ের গৌরবের পথে, তাঁর কবিতা সহজে কোনো পত্রিকা ছাপতে চাইছিল না, বোদলেয়ারের মনে হচ্ছিল অস্বীকার ও যন্ত্রণালাভের মধ্যে দিয়ে তাঁর স্খালন ঘটছে, কবিতায় ইতরতার সঙ্গে সৌন্দর্যের মিশেলে গড়া তাঁর পাঠবস্তুতে তিনি তাঁর প্রতি ঈশ্বরের অবিচারের প্রসঙ্গ তুলেছেন । তিনি এডগার অ্যালান পো-কে ফরাসী পাঠকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার সময়ে পো-এর জীবনেও মদ্যপানের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন, যা তাঁর জন্য হয়তো জীবনবিনাশী ছিল, কিন্তু তা তাঁকে করে তুলেছিল প্রকৃত সৃজনশীল মানুষ, কেননা, বোদলেয়ারের মতে, পো কখনও নেশাহীন প্রকৃতিস্হ থাকতে চাইতেন না । বদল্যার বলেছেন যে পো সাধারণ মানুষের মতন মদ খেতেন না, খেতেন বর্বরদের ঢঙে, মার্কিনী তেজে, যাতে এক মিনিট সময়ও নষ্ট না হয়, যেন তিনি খুন করার জন্য তৈরি, এমন একটা পোকাকে খুন করতে চাইছেন যা তাঁর ভেতরে বাসা বেঁধে আছে আর মরতে চায় না ।
বদল্যারের মতে, মত্ততা এডগার অ্যালান পো-কে কেবল যে মহান কবি করে তুলেছে, তা নয়, তাঁকে করে তুলেছে মহান মানুষ ; পো-এর মত্ততা ছিল স্মৃতিবর্ধনের ক্রোনোট্রোপ ( সময়/পরিসর ), সাহিত্যকর্মের খাতিরে একটি সুচিন্তিত ও স্বেচ্ছাকৃত উপায়, তা মারাত্মক দুর্দশাপূর্ণ হলেও, তাঁর স্বভাবচরিত্রের সঙ্গে খাপ খেয়ে গিয়েছিল । ভেরলেন যেমন বদল্যারের মাধ্যমে গড়ে তুলেছিলেন আত্মক্ষয়ের গৌরবের কিংবদন্তি, একই ভাবে বদল্যার আত্মক্ষয়ের গৌরবের কিংবদন্তি গড়ে তুলেছিলেন এডগার অ্যালান পো-এর মাধ্যমে ।
উনিশ শতকের ফ্রান্সে যে কবিদের রচনা আধুনিক বিশ্ব সাহিত্যকে রূপ দিয়েছে, তাঁদের প্রতি ফরাসি প্রাতিষ্ঠানিকতার দুর্ব্যবহার ব্যাখ্যার অতীত । ভেরলেন যাঁদের অভিশপ্ত কবি হিসাবে চিহ্ণিত করেছেন, তাঁদের সঙ্গে ভেরলেনের জীবনযাত্রা বেছে নেয়ায় পার্থক্য আছে । আবসাঁথের নেশার প্রতি ভেরলেনের টানের কারণ তিনি তাঁর ‘স্বীকৃতি’ বইতে জানাননি, এবং আবসাঁথ খাবার পর যে সমস্ত দানবিক আচরণ তিনি করতেন তারও কোনো ব্যাখ্যা নেই । অনেকে মনে করেন তাঁর বাবার পালিত মেয়ে এলিজা তাঁর সঙ্গে সঙ্গমের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের কারণে ভেরলেন হীনম্মন্যতায় ভুগতে আরম্ভ করেন এবং আত্মধ্বংসের দিকে এগিয়ে যান । পরবর্তীকালে তিনি তো যথেষ্ট রয়ালটি পেতেন এবং তা থেকে তিনি নিশ্চয়ই তাঁর পাঠকের সংখ্যাবৃদ্ধি আঁচ করে থাকবেন ।
র্যাঁবোর অভিশপ্ত হবার কারণ পাওয়া যায় বাবার অনুপস্হিতিতে । তাঁদের পাঁচ ভাইবোনের কারোর জন্মের সময়ে তাঁর বাবা বাড়িতে ছিলেন না । তাঁর যখন ছয় বছর বয়স তখন তাঁর বাবা তাঁদের ছেড়ে চলে যান, ফলে শৈশব থেকে তাঁকে আর তাঁর মাকে টিটকিরি শুনতে হতো। তাঁর মা নিজেকে বলতেন বিধবা । অনুপস্হিত বাবাকে ঈশ্বরের আসনে বসিয়ে র্যাঁবো ঈশ্বরনিন্দা ও খ্রিস্টধর্মকে আক্রমণ করেছেন তাঁর কবিতায় । ঈশ্বরই তাঁর ও তাঁর মায়ের দুঃখদুর্দশার জন্য দায়ি । সেই অনুপস্হিত বাবাকে তিনি প্যারিসের অগ্রজ কবিদের মধ্যে পেতে চেয়ে অবহেলিত হন ।
ভেরলেনও জেলে থাকার সময়ে রোমান ক্যাথলিক ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন, তবু তিনি ঈশ্বরভক্তি ও ঈশ্বরনিন্দার মাঝে দোটানায় পড়ে কবিতা লিখেছেন । খ্রিস্টধর্মের প্রফেটদেরও যেহেতু যন্ত্রণাভোগ করতে হয়েছে, যিশুকে ক্রূশকাঠে পেরেকে গেঁথা অবস্হায় ঝুলতে হয়েছে, তাই একজন কবিও, যে মানবসমাজের জন্য কবিতা লিখছে, তাকেও প্রফেটদের মতন অভিশপ্ত জীবন কাটাতে হবে, মনে করেছেন ভেরলেন । আঘাত পাওয়াকে তাঁরা অপরিহার্য সত্য বলে মান্যতা দিয়েছেন । রসাস্বাদন করেছেন শহিদত্বের, জাহির করেছেন তাকে । মন্দভাগ্যের সাধনা তাঁদের অন্তরজগতকে বড়ো বেশি দখল করে নিয়েছিল, বিশেষ করে ভেরলেনের । খ্রিস্টধর্মমতে মানসিক অবস্হানটি ‘ইপিফ্যানি’ । এই মনস্হতিকে অ্যারিস্টটল বলেছিলেন ‘দৈব উন্মাদনা’, ইউরোপীয় রেনেসাঁর গবেষক বলেছিলেন ‘শনিআক্রান্ত স্বভাবচরিত্র’।
যাঁরা আচমকা সেই ইপিফ্যানিতে আক্রান্ত হন, তাঁরা, ‘বিশুদ্ধ’ অভিজ্ঞতার খাতিরে, মনের ভেতরে সন্ধান করেন সীমাহীনতার, যে পরিসরে তিনিই নিজেকে মনে করেন সর্বেসর্বা, আত্মক্ষয় তাঁর কিচ্ছু করতে পারবে না ; মাদক, যৌনতা, মৃত্যু, ধর্মহীনতা, কোনো কিছুই তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারবে না, কেননা তিনি আত্মক্ষয়ের গৌরবে আহ্লাদিত পরিসরের সার্বভৌম মালিক । সেই গায়ক, কবি, চিত্রকর, ভাস্কর, স্হপতির আহ্লাদের শক্তিক্ষমতা, তাঁদের যন্ত্রণাদায়ক যাত্রাপথে এগোনোয় প্ররোচিত করে ; তাঁরা জানেন যে প্রয়াস না করলে তাঁরা কিছুই নন, তাঁরা একজন ‘নেইমানুষ’ ।
যৌনতা তাঁদের কাছে বংশরক্ষার অথবা সন্তানের জন্ম দেবার প্রক্রিয়া নয়, যেমন মাদক নয় নেশাগ্রস্ত থাকার জন্য, এগুলো তাঁদের ‘নেইমানুষ’ হতে দেয় না । বংশরক্ষা বা সন্তানোৎপাদনের যৌনতা, ব্যক্তিঅস্তিত্বকে ধারাবাহিকতার বাইরে নিয়ে যায়, গতানুগতিকতায় বেঁধে ফ্যালে। ধারাবাহিকতাহীনতা হলো অভিশপ্ত কবিদের প্রতিদিনের জীবনের সাধারণ স্বাভাবিক ঘটনা । জনসাধারণের মাঝে একজনের সঙ্গে আরেকজনের বাধা থাকে, অনেকসময়ে দূরতিক্রম্য, ধারাবাহিকতাহীনতা থাকে, পতিত-অঞ্চল থাকে । মানুষের ব্যক্তিএকক-বোধ জন্মায় তার সামনের বস্তুপৃথিবীর জিনিসগুলোর ব্যবহারের কারণে — তাদের দরুণ বস্তুদের থেকে সে বিচ্ছিন্ন থাকে । ‘নেই-বোধ’ হলো অস্তিত্বের ধারাবাহিকতা, এবং এই ধারাবাহিকতার সন্ধান করেন আত্মক্ষয়ের আহ্লাদে আক্রান্ত অভিশপ্ত কবিরা । ‘নেই-বোধ’ হলো অহং-এর সমাপ্তি, যা মানুষটি ঝেড়ে ফেলতে চাইছেন, এবং সেই কারণেই আশেপাশের জনসাধারণকে সরিয়ে দিতে চাইছেন ।
অমন মানুষটি আত্মবলিদানের গোমরে ভুগছেন কেন ? কেননা তাঁর কাছে আত্মবলিদানের গোমর হলো কেবলমাত্র ধ্বংস, তা নিশ্চিহ্ণ হওয়া নয় । আত্মবলিদানের গোমর বস্তুদের প্রতি আনুগত্যকে ধ্বংস করে ; প্রয়োজনীয় দৈনন্দিনের উপযোগীতাবাদী জীবন থেকে টেনে বের করে আনে, এবং মানুষটিকে প্রতিষ্ঠা করে দুর্বোধ্য খামখেয়ালে , স্বকীয় পবিত্রতায়, যার খোলোশা কেবল তিনিই করতে পারবেন । তাঁর এই ‘বিশুদ্ধ অভিজ্ঞতা’ ঘটে তাবৎ সীমাগুলোর বিদারের মাধ্যমে, যাবতীয় নিষেধ অতিক্রমের দ্বারা, যা তাঁকে একযোগে আহ্লাদ ও পীড়নের স্হিতিতে নিয়ে গিয়ে একাকী ছেড়ে দেয় । ‘বিশুদ্ধ অভিজ্ঞতা’ হলো ‘নেই-স্হিতি’, এবং সেহেতু মানসিক ও দৈহিক আত্মক্ষয় সম্পূর্ণ পরিবর্তন-পরিশীলনের জন্য একান্তই জরুরি । অভিশপ্ত কবির ভেতরে-ভেতরে যে সন্ত্রাস চলছে তা অন্য কেউ তাঁকে দেখে বুঝতে পারে না ; তার জন্য তাঁর গানে, সঙ্গীতে, কবিতায়, ভাস্কর্যে, পেইনটিঙে, স্হাপত্যে, প্রবেশ করতে হবে ।
ব্যক্তিএককের বিশুদ্ধ অভিজ্ঞতার ক্রোনোট্রোপে বাস্তব জগত আর মিথ মিলেমিশে গেলে তার যে মানসিক অবস্হা গড়ে ওঠে তাকে ভেরলেনের আলোচকরা বলেছেন ‘নুমিনাস’, যে অবস্হায় ব্যক্তিএককের অন্তরজগতে নিদারুণ তোলপাড় ঘটতে থাকে, সে তখন বাইরের জগতের প্রতি উৎসাহহীন, তার মনে হয় সে বাইরের জগতের দ্বারা অবদমিত, হতোদ্যম অবস্হায় সে নিজের ভেতরে আরও বেশি করে ঢুকে যেতে থাকে, তখন সে বিপজ্জনক আত্মক্ষয়ের স্বাদ পেতে আরম্ভ করেছে, খাদের কিনারে পৌঁছে গেছে, বুঝে উঠতে পারছে না ঝাঁপ দেবে নাকি ফিরে যাবে ।
সুইডেনের নাট্যকার অগাস্ট স্ট্রিণ্ডবার্গ, যিনি খাদের কিনারায় গিয়ে ফিরে এসেছিলেন, বেশ কিছু সময় মানসিক হাসপাতালে ছিলেন, তিনি নিজের অবস্হাটা যাচাই করে বলেছিলেন যে, ‘যারা উন্মাদ হবার সুযোগ পায় তারা যথেষ্ট ভাগ্যবান’ । মার্কিন কবি জন বেরিম্যান, যাঁর বাবা শৈশবে নিজেকে গুলি করে আত্মহত্যা করেছিলেন, এবং যিনি বাবার আত্মহত্যার স্মৃতি থেকে কখনও মুক্তি পাননি , বলেছিলেন, ‘যে কবি অত্যন্ত ভয়াবহ মানসিক চাপের মধ্যে দিয়ে গেছে, যা তাকে মেরে ফেলতে পারতো অথচ যা তাকে প্রকৃতপক্ষে বাঁচতে সাহায্য করেছে, তার অদৃষ্টের প্রশংসা করা উচিত’।
অভিশপ্ত কবির ভেতরে এক সৃজনশীল ক্ষমতা প্রবেশ করে ; সে চেষ্টা করে যায় যাতে বিস্ফোরণে সে নিজেই না উড়ে শতচ্ছিন্ন হয়ে যায়, সে চেষ্টা করে কখন সৃজনশীলতার আবেগ ও সংবেদনকে প্রয়োগ করতে হবে । সব সময় একটা ভীতি কাজ করে, কেননা সৃজনশীল মানুষটি খাদের ধার পর্যন্ত যাবেনই, আবার একই সঙ্গে তাঁর ভেতর এই ভীতি কাজ করে যে তিনি বড়ো বেশি মার্জিত রুচিশীল বিবেকী সুস্হতাবিশিষ্ট স্হিরমস্তিষ্ক হয়ে উঠছেন না তো ! সাধারণ মানুষের তুলনায় সৃজনশীল মানুষ, নিজের সৃজনশীলতার সঙ্গে আপোষ করতে না পেরে খানিকটা ম্যানিক-ডিপ্রেসিভ হয়ে পড়েন, এবং ম্যানিক-ডিপ্রেসিভ হবার কারণে তাঁরা যখন ডিপ্রেশানে আক্রান্ত হন তখন, সাধারণ মানুষের তুলনায়, অস্তিত্বের সমস্যাগুলোর মুখোমুখি হতে পারেন, অন্তদর্শী হতে পারেন, প্রতিক্ষেপক হতে পারেন । আমেরিকায় লেনি ব্রুস নামে একজন প্রতিসাংস্কৃতিক কমেডিয়ান ছিলেন, অশ্লীল ভাষায় সবায়ের সমালোচনা করতেন, যে কারণে তাঁকে কারাদণ্ড দেয়া হয়েছিল, এবং তাঁর মৃত্যুর পর তা মাফ করে দেয়া হয়, তিনি উন্মাদ বুদ্ধিমত্তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ, তাঁকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়নি, তিনি নিজেও আত্মক্ষয়ে ভোগেননি ।
ডাক্তারি ভাষায় আত্মক্ষয়ের গৌরবকে বলা হবেছে ‘হাইপোম্যানিয়া’ । কোনো সৃজনশীল মানুষকে যদি হাইপোম্যানিয়ার স্বীকৃতি দেয়া হয় তাহলে তাঁর কাছে তা সৃজনের স্বাধীনতাপ্রাপ্তি । সৃজনশীল মানুষ তাঁদের কাজের জন্য যে কাঁচা মাল ব্যবহার করেন, তা আসে তাঁদের অন্তর্জীবনের বুনিয়াদি বা আদিকালীন স্তর থেকে — যৌন কল্পনা, পূর্বপক্ষতা, আগবাড়া চারিত্র্য, বহুবিধ যৌনাঙ্গিকের ভাবনা থেকে । শৈশব থেকে মানুষের ভেতরে এই বোধগুলো কাজ করে, সে এই স্তরগুলো অতিক্রম করে যৌবনে পৌঁছোয় । বয়সের সঙ্গে সে আত্মনিয়ন্ত্রণ করতে শেখে, আদিম-চেতনাকে দাবিয়ে রাখতে শেখে, সামাজিক বাধানিষেধকে মান্যতা দিতে শেখে । কিন্তু সৃজনশীল মানুষ এগুলোর সংস্পর্শে থাকেন, আর তাদের বোঝার জন্য নিজের সঙ্গে লড়তে থাকেন, আর নিজের আদিম চারিত্র্যের সঙ্গে সংস্পর্শে থাকার অভিপ্রায়ে তিনি উন্মাদনা ও মতিস্হিরতার মাঝে ভারসাম্য বজায় রেখে চলেন আবার কখনও বা সেই ভারসাম্য হারিয়ে অভিশপ্ত হন।
তিন
পল-মারি ভেরলেনের জন্ম ১৮৪৪ সালের ৩০ মার্চ উত্তরপূর্ব ফ্রান্সের মোৎসেল আর সেইলি নদীর সঙ্গমস্হল মেৎজ শহরে । সমরবাহিনীর ক্যাপ্টেন তাঁর বাবা নিকোলাস অগুস্তে ভেরলেন ১৮৫১ সালে মেৎজ থেকে প্যারিসে পাকাপাকি বসবাসের জন্য চলে যান । সেখানে পল ভেরলেনকে বোনাপার্ত উচ্চবিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয় । স্কুলের তথ্য অনুযায়ী চোদ্দো বছর বয়সে তাঁকে দেখতে কুৎসিত মনে হতো । জীবনের প্রথম সাত বছর বাবার চাকুরির দৌলতে বিভিন্ন শহরে বসবাস করতে হয়েছিল ভেরলেনকে, যার দরুণ শৈশবে তাঁর একমাত্র বন্ধু ছিলেন তাঁদের বাড়িতে আশ্রয় নেয়া খুড়তুতো বোন এলিজা । এলিজার অকালমৃত্যু মেনে নিতে পারেননি কিশোর ভেরলেন ; এলিজা ছিলেন তাঁর প্রথম প্রেম, যদিও এলিজার বিয়ে হয়ে গিয়েছিল আর একটা বাচ্চা ছিল তবু ভেরলেন তাঁকে দৈহিকভাবে চেয়েছিলেন; এলিজাকে নিয়ে লেখা তাঁর ‘দুর্দান্ত উৎসব’ প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৬৯ সালে, এলিজার মৃত্যুর পর ।
১৮৬২ সালে স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ভেরলেন প্রথমে বীমা কোম্পানির চাকুরিতে যোগ দেন। ১৮৬৫ সালে তাঁর বাবা মারা যান । দুই বছর আইন পরীক্ষা পড়ার পর ছেড়ে দ্যান। ১৮৬৭ সালে এলিজা মোনকোঁলের মৃত্যুর ফলে তিনি নিজেকে নিঃসঙ্গ বোধ করতে থাকেন আর বেয়াড়া হয়ে যান, বাবা-মায়ের কাছে তাঁর আবদার বেড়ে যায়, খামখেয়ালি, অব্যবস্হিতচিত্ত, স্বার্থপর, অপরিণত যুবক হয়ে ওঠেন । তাঁর মা মদ খাবার টাকা যোগাতেন না বলে বাড়িতে প্রায়ই ঝগড়া হতো । উচ্চবিদ্যালয়ে পড়ার সময় থেকেই তাঁর আবসাঁথ খাবার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল । মদ্যপ অবস্হায় দু’বার মাকে খুন করার জন্য তাঁর পেছনে তরোয়াল নিয়ে দৌঁড়েছিলেন । ভেরলেনের বন্ধু তাঁদের দুজনের মাঝে গিয়ে ভেরলেনকে কাবু করেন । মাকে দ্বিতীয়বার আক্রমণের ব্যাপার চলেছিল সাত ঘণ্টা কথা কাটাকাটির মাঝে । মা পরের দিন সবকিছু ভুলে গিয়ে আদরের ছেলেকে ক্ষমা করে দিতেন ।
শার্ল বোদলেয়ারের ‘পাপের ফুল’ ( Les fleurs du mal ) পড়ার পর পল ভেরলেনের কবিতা লেখার ইচ্ছা হয়। ১৮৬৩ সালে তাঁর প্রথম কবিতা ‘মসিয়ঁ প্রুধোম’ প্রকাশিত হয় । তিনি ‘সমসাময়িক কবিতা’ ( Le Parnasse Contemporain ) পত্রিকার সম্পাদক কাতুলে মেনদেস-এর সঙ্গে দেখা করেন । পত্রিকাটিতে তাঁর আটটি কবিতা প্রকাশিত হয় । উনিশ শতকের ফ্রান্সে একদল কবি আরম্ভ করেন পারনাসিয় আন্দোলন ; নামটি নেয়া হয়েছিল অ্যাপোলো আর মিউজদের পবিত্র গ্রিক পাহাড়ের নাম থেকে । পারনাসিয়রা বিষয়বস্তু এবং শৈলীর বিস্তার প্রদর্শন করলেও, তাঁরা গুরুত্ব দিয়েছেন কারিগরি, অশেষ সৌন্দর্য ও বস্তুনিষ্ঠাকে। রোমান্টিসিজমের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসাবে দেখা দিয়েছিল পারনাসিয় আন্দোলন এবং তা ক্রমে প্রসারিত হয় প্রতীকবাদ ও ডেকাডেন্ট কাব্যিক ঐতিহ্যে । পারনাসিয় আন্দোলনের প্রধান কবি বলে মনে করা হয় শার্ল-মারি-রেনে লেকঁত দ্যলিজেকে, কিন্তু আন্দোলনের অংশ হিসাবে মান্যতা দেয়া হয় থিয়োদোরে দ্যবাঁভিল, অঁরি কাজালিস, ফ্রাঁসোয়া কোপি, আনাতোল ফ্রাঁসে, থিয়োফিল গতিয়ে, জোসে-মারিয়া দ্যহেরদিয়া, সালধ প্রুধোম, পল ভেরলেন ও শার্ল বোদলেয়ারকে। ১৮৬৬, ১৮৭১ ও ১৮৭৬ সালে সবসুদ্ধ নিরানব্বুইজন কবির তিনটি সংকলন প্রকাশ করেন আলফোঁসে লেমেরে, কাতুলে মেন্দেস আর লুই জেভিয়ার । এই তিনটি সংকলনের প্রকাশকে ফরাসী সাহিত্যে বাঁকবদলকারী ঘটনা বলে মনে করা হয় । তবে থিয়োফিল গতিয়ে যখন ‘আর্ট ফর আর্টস শেক’ স্লোগান দিলেন তখন পারনাসিয় কবিরা একটা বৌদ্ধিক গতিমুখ পেলেন । ভেরলেন নিজেকে পারনাসিয় আন্দোলনের একজন সদস্য বলে মনে করতেন না ।
১৮৬৬ সালে প্রকাশিত হয় ভেরলেনের প্রথম কাব্যগ্রন্হ Poemes Saturniens এবং দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্হ Gallant Parties প্রকাশিত হয় ১৮৬৯ সালে । মেনদেসের মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে অন্যান্য পারনাসিয় কবি লেকঁতে দ্যলিজে, থিয়োদির দ্য বাঁভিল, লুই জেভিয়ার দ্য রিকার্দ, ফ্রাঁসোয়া সিপ্পি প্রমুখের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় এবং সুফলো রোড-এর সস্তা মদের দোকানে সবাই মিলে আড্ডা দিতেন । বিয়ারের স্বাদ সেসময়ে ভালো ছিল না বলে আবসাঁথের প্রতি আসক্ত হন ভেরলেন ও অন্যান্য কবিরা । ভেরলেন নিজেই ‘স্বীকৃতি’ বইতে জানিয়েছেন যে তিনি একবার সারারাতে দুশোবার অর্ডার দিয়ে আবসাঁথ খেয়েছিলেন । Poemes Saturniens এর “হেমন্তের কবিতা” লিখে ভেরলেন কবিদের প্রশংসা পেয়েছিলেন এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে এই কবিতাটির প্রথম ছয় লাইন মিত্রপক্ষের সৈন্যবাহিনী নরম্যাণ্ডি অবতরণের কোড হিসাবে বিবিসি থেকে প্রসার করেছিলেন ; প্রথম তিন লাইন পয়লা জুন আর দ্বিতীয় তিন লাইন পাঁচুই জুন :
হেমন্তের বেহালার
দীর্ঘ ফোঁপানিগুলো
আমার হৃদয়কে আহত করে
একঘেয়ে সুরের অবসাদে ।
সমস্তকিছু শ্বাসহীন
আর ফ্যাকাশে, যখন
সময়ের কাঁসর বেজে ওঠে,
আমার মনে পড়ে
বিগত দিনগুলো
আর আমি কাঁদি
আর আমি চলে যাই
এক অশুভ বাতাসে
যা আমাকে নিয়ে যায়
এখানে, সেখানে,
যেন গাছের এক
মৃত পাতা ।
বাইশ বছর বয়সে লেখা কবিতাটির শিরোনাম যদিও ‘হেমন্তের গান’, প্রতীকবাদী অন্যান্য কবিদের মতো ভেরলেনও, র্যাঁবোর সঙ্গে পরিচয়ের আগে, ‘আর্ট ফর আর্ট সেক’কে মান্যতা দিয়ে কবির অন্তরজগতকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন এবং তিনি যে বলতেন কবিতাকে সঙ্গীতময় হয়ে উঠতে হবে, তার পরিচয় মেলে এই কবিতায় ; তিনি বলতেন যে কবিতায় সঙ্গীতই প্রথম এবং প্রধানতম । যাঁরা কবিতাটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন, তাঁদের বক্তব্য, ফরাসি ভাষায় না পড়লে কবিতাটির সঙ্গীতময়তা অনুধাবন করা যায় না । এই কবিতাটির অনুকরণে উনিশ শতকের শেষ দিকে বহু কবি কবিতা লিখেছেন । এই কবিতার আনুয়ি বা অবসাদ হয়ে ওঠে ভেরলেনের কবিতার বৈশিষ্ট্য। ভেরলেনের কবিতায় ক্ষয় বা অপচয় ঘুরে-ঘুরে এসেছে । কবিতাটির ধীর লয় কবির অবসাদকে তুলে ধরার জন্য প্রয়োগ করেছেন ভেরলেন । পারনাসিয় কবিদের প্রভাবে র্যাঁবো ‘দি ড্রাঙ্কন বোট’ বা ‘মত্ত নৌকো’ নামে একটা কবিতা লিখেছিলেন, কিন্তু পরে নিজেই এই কবিতার ধারাকে সমর্থন করেননি, এবং গদ্যকবিতার দিকে ঝোঁকেন ।
উনিশ শতকের প্যারিসে লাতিন কোয়ার্টার ছিল যেন এক বোহেমিয়ান দ্বীপ, যেখানে জড়ো হতেন অজস্র লেখক, শিল্পী, নাট্যকার আর কবিযশোপ্রার্থী । ভিক্তর য়োগো, শার্ল বোদলেয়ার প্রমুখের মতন পল ভেরলেনও বেছে নিয়েছিলেন এলাকাটা, সস্তার মদ আর বেশ্যাসঙ্গের আকর্ষণে । প্যারিসের ইতিহাসে এই সময়টাই ছিল প্যারিস কোয়ার্টারের খ্যাতি-কুখ্যাতির কারণ -- এখন তা একেবারে বদলে গিয়েছে । যারা এই এলাকায় বাস করতো তাদের কাছে পাড়াটা ছিল নরক । অত্যন্ত গরিব শ্রমজীবিদের পাড়া, দুবেলা খাবার জোটেনা, অসুখে পড়লে বিনা চিকিৎসায় মারা যেতে হয় ইত্যাদি । তারা প্রধানত গ্রামাঞ্চল থেকে এসে সস্তায় থাকার জায়গা হিসাবে বেছে নিয়েছিল পাড়াটা, আর বাড়তি রোজগারের জন্য ঘর ভাড়া দিতো, বেশ্যাগিরি করতো, সস্তার মদ বিক্রি করতো । ক্রমশ তারা লেখক-কবি-শিল্পীদের চাহিদা মেটাবার জন্য সারারাতের যৌনহুল্লোড়ের ব্যবস্হা করতো । ফরাসি সাহিত্যে দেখা দিচ্ছিল রোমান্টিক ঔপন্যাসিকদের জনপ্রিয়তা, আদর্শের পরিবর্তে ‘পাপের ফুলের’ বা ‘নরকে ঋতুর’ প্রতি আকর্ষণ । ফাউস্তের জায়গা নিয়ে নিচ্ছিল মেফিসতোফিলিস । ঈশ্বর-বিশ্বাস নিয়ে দোটানায় ছিলেন কবি-লেখক-শিল্পীরা । পেত্রুস বোরেল নামে এক কবি, যিনি বোদলেয়ারের বন্ধু ছিলেন, লাতিন কোয়ার্টারে গরিব সেজে ঘুরে বেড়াতেন, তাঁকে বলা হতো “নেকড়ে বাঘে পরিণত মানুষ।”
ভেরলেনের মতিগতি ফেরাবার জন্য তাঁর মা তাঁর বিয়ে প্রথমে ঠিক করেন কড়া মেজাজের এক মামাতো বোনের সঙ্গে, কিন্তু তা এড়াবার জন্য ভেরলেন পছন্দ করেন এক বন্ধুর সৎবোন, তাঁর চেয়ে বয়সে বেশ ছোটো সুন্দরী তরুণী মাতিলদে মত দ্য ফ্ল্যেওরভিলেকে, বিয়ে হয় ১৮৭০ সালে ; মাতিলদের সঙ্গে পরিচয়ের সময়ে যুবতীটির বয়স ছিল ষোলো, তাঁর মা-বাবা ভেরলেনকে জানান যে তাঁকে এক বছর অপেক্ষা করতে হবে । ১৮৬৯ সালের জুনমাসের এক দুপুরে, মদ খাবার জন্য বন্ধু শালর্ক দ্য সিভরির মমার্তর বাড়িতে গিয়েছিলেন পল ভেরলেন । শার্ল তাঁর মা আর সৎবাবা থিওদোর মতে দ্য ফ্লেওরভিলের সঙ্গে থাকতেন । দুই বন্ধু যখন গল্প করছিলেন তখন ষোলো বছরের একটি সুন্দরী যুবতী ঘরে ঢোকেন, ভেরলেনের মতে ইচ্ছাকৃতভাবে ঢোকেন, তিনি শার্লের সৎবোন মাতিলদে মতে । ভেরলেনের কবিতা তাঁর পড়া ছিল এবং পড়ে কবিকে ভালো লেগেছিল, তিনিও ভেরলেনের প্রেমে পড়েন । বিয়ের ছয় মাসের মধ্যেই মাতিলদে গর্ভবতী হবার দরুন ভেরলেন বিষাদে আক্রান্ত হয়ে আবার লাতিন কোয়ার্টারে যাতায়াত আরম্ভ করেন ।তাঁদের একটি ছেলেও হয় ।
মাতিলদে এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন যে প্রথম দুই বছর ভেরলেন তাঁকে খুব ভালোবাসতেন এবং তাঁকে নিয়ে অনেক কবিতা লিখেছিলেন। ভেরলেনের তৃতীয় কাব্যগ্রন্হ ‘ভালো গান’-এর কবিতাগুলো মাতিলদেকে মনে করে লেখা । কিন্তু মাঝে-মাঝে ভেরলেনের রুদ্ররূপ বেরিয়ে পড়তো আর তিনি মাতিলদের গায়ে হাত তুলতেন । একবার তিনি মাতাল অবস্হায় তাঁর ছেলে জর্জকে তুলে দেয়ালে মাথা ঠুকে দিয়েছিলেন । তাঁর মা, শশুর-শাশুড়ির উপস্হিতিতেও এরকম আচরণ করতেন তিনি ।
ভেরলেন মিউনিসিপালিটির সরকারি চাকরিতে যোগ দেন ১৮৭০ সালে । কিন্তু তৃতীয় নেপোলিয়ানের পতনের পরবর্তী দ্রোহের সময়ে প্যারিস-শহর ও চাকরি ছেড়ে পালান । ১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৭০ থেকে ২৮ জানুয়ারি ১৮৭১ পর্যন্ত প্রুসিয় সেনারা প্যারিস শহর ঘিরে ফরাসিদের জব্দ করতে চায় । সমস্ত কিছুর অভাব দেখা দেয় । কবি-লেখকরা লাতিন কোয়ার্টারের যে পাড়ার পানশালায় গিয়ে আড্ডা দিতেন সেখানেের ভোজন-তালিকায় ঘোড়া, কুকুর, বিড়াল এমনকি ইঁদুরের মাংস বিক্রি হতো । নারী আর পুরুষ বেশ্যারা এই খাবার একপেট খাবার বিনিময়ে সঙ্গমে রাজি হয়ে যেতো । এই সময় খবর রটে যায় যে বিসমার্ক পরামর্শ দিয়েছেন প্যারিসের ওপরে চারিদিক থেকে কামান দাগা হোক, কিন্তু ব্লুমেনথেল তা সামলে দেন এই তর্কে যে ফরাসি সেনার বদলে সাধারণ মানুষ তাতে মারা পড়বে । ভেরলেনসহ অনেকেই, যাঁরা প্যারিস কমিউনে যোগ দিতে চাননি, তাঁরা প্যারিস ছেড়ে পালান । ভেরলেন অবশ্য কমিউনের প্রেস অফিসার হিসাবে ১৮৭০-এ কাজ করেছিলেন আর কমিউন ভেঙে যাবার পর রাস্তায়-রাস্তায় খণ্ডযুদ্ধ আরম্ভ হলে অন্যান্য কবি-লেখকদের সঙ্গে গা ঢাকা দেন ।
পল ভেরলেনের জীবনযাত্রা, অপরাধ আর সাধাসিধে ছলাকলাশূন্যতার মাঝে দোল খেয়েছে । স্তেফান মালার্মে ও শার্ল বোদলেয়ারের সঙ্গে তাঁকে প্রতীকবাদী কবিতার ত্রিমূর্তির অন্তর্গত করলেও, দুটি প্রতীতি প্রাধান্য পায় : প্রথম হল যে কবির অহং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ; দ্বিতীয় যে কবিতার কাজ হল চরম সংবেদন ও একক ধৃতির মুহূর্তগুলোকে অক্ষুণ্ণ রাখা । Poemes saturniens ( ১৮৬৬ ) কাব্যগ্রন্হে তিনি প্রশ্ন তুলেছিলেন, “একে মিলোর তৈরি ভেনাস বলা হবে নাকি নিছক শ্বেতপাথর ?” তাঁর কবিতায় আপাত-অনিশ্চয়তা ও অস্পষ্টতা সত্বেও, তিনি কবিতার কারিগরিতে সহজ ও সঙ্গীতময় শব্দ প্রয়োগ করে সাবধানি কারুনৈপূণ্য বজায় রেখেছেন । ফরাসি ধ্রুপদি কবিতার খোলোসের মধ্যে থেকেও ছন্দবর্জনের খেলা খেলেছেন, যেমন ১৮৭৪-এ রচিত Romances sans Paroles কবিতায় লিখেছেন :
“আমার হৃদয়ে ক্রন্দন
শহরে বৃষ্টি পড়ার মতো”
মাতিলদেকে নিয়ে ভেরলেন ভালোবাসার অনেকগুলো কবিতা লিখেছিলেন Le bonne chanson ( The Good Song ) কাব্যগ্রন্হে । কয়েকটার বাংলায়ন :
এক নারীসন্ত তাঁর জ্যোতিতে
এক নারীসন্ত তাঁর জ্যোতিতে,
এক গিন্নিমা তাঁর মিনারে,
মহিমা ও ভালোবাসা
যা মানুষের শব্দাবলীতে আছে ;
সোনার বার্তা যা বাঁশি
বহুদূরের বনানী থেকে বাজায়,
অবলা গর্বের সঙ্গে বিবাহিত
যা বহুকাল আগের মহিমাময়ীদের ;
তার সাথে, ধরা পড়ে না এমন সৌন্দর্য
এক তরতাজা বিজয়িনী হাসির
যা ফুটে উঠেছে রাজহাঁসের পবিত্রতায়
আর এক নারী-শিশুর লজ্জায় ।
মুক্তার মতো আদল, শাদা আর গোলাপি,
এক মৃদু অভিজাত স্বরসঙ্গতি :
আমি দেখি, আমি এই সবকিছু শুনতে পাই
মেয়েটির শার্লমেনিয় বংশধরের নামে ।
আমি অধর্মের পথে গিয়েছিলুম ...
আমি অধর্মের পথে গিয়েছিলুম,
বেদনাদায়ক অনিশ্চিত
তোমার প্রিয় হাত ছিল আমার পথনির্দেশক।
তাই দূরে দিগন্তের উপর ফ্যাকাশে
ভোরের একটি দুর্বল আশা ছড়াচ্ছিল দ্যুতি;
তোমার দৃষ্টিতে ছিল ভোর।
চারিদিক নিঃশব্দ, তোমার সুরেলা পদক্ষেপ ছাড়া শব্দ নেই,
ভ্রমণকারীকে উত্সাহিত করেছো তুমি।
তোমার কন্ঠস্বর আমাকে বলেছিল: "এগিয়ে চলো !"
আমার ভয়ঙ্কর হৃদয়, আমার ভারী হৃদয়
একা কেঁদেছিল দুঃখের পথযাত্রায়
ভালবাসা, আনন্দদায়ক বিজয়ী,
আমাদের আনন্দের বাঁধনে আবার একত্র করেছে।
১৮৬৫ সালে শার্ল বোদলেয়ার সম্পর্কে লেখা দুটি প্রবন্ধে ভেরলেন জানিয়েছিলেন যে একজন কবির অন্বেষন কেবল সৌন্দর্য । কবিতা রচনায়, তিনি বলেছেন, প্রেরণা আর আবেগের যৎসামান্য স্হান থাকলেও কবির থাকা দরকার কারিকুরির সৃষ্টিশীলতা । ব্যক্তিগত আবেগকে যদি ব্যবহার করতে হয় তাহলে ছন্দ, ধ্বনি এবং চিত্রকল্পকে একত্রিত করে একটি কাব্যিক সঙ্গীত গড়ে নিতে হবে এবং সেই জগতে কোনোকিছুই আপতনিক নয় । ভেরলেনের কারিগরির ফল হল তাঁর কবিতার সঙ্গীতময়তা ; ধ্বনিরা একত্রিত হয়ে এক সুরেলা ঐকতান সৃষ্টি করে । ১৮৮২ সালে তিনি বলেছিলেন, “L’Art poetique” কবিতায়, “কবির উচিত বিজোড়-মাত্রার পঙক্তি, যথাযথ-নয়-এমন শব্দভাঁড়ার এবং প্রচ্ছন্ন চিত্রকল্প ব্যবহার করা ; রঙের বদলে অতিসূক্ষ্ম তারতম্যকে গুরুত্ব দেয়া । কবিকে ইচ্ছাকৃত ছন্দ, বৈদগ্ধ্য ও বাগ্মীতা এড়াতে হবে । কবিতা হবে হালকা, বাতাসে ভাসমান, যৎসামান্য সুগন্ধময় ও ক্ষণিক । এছাড়া সমস্তকিছু কবিতা হয়ে ওঠার পরিবর্তে হয়ে উঠবে সাহিত্য ।”
সমসাময়িক বাস্তববাদ এবং বাগাড়ম্বরপূর্ণ অলঙ্কার বর্জন করে অন্যান্য প্রতীকবাদী কবিদের মতো পল ভেরলেনও উদ্দীপিত করতে চেয়েছেন মেজাজ, সত্তা । তাঁর কাব্যগ্রন্হ Fetes gallantes এর অন্তর্গত Clair de Lune ( Moonlight ) “চাঁদের আলো” কবিতাটিকে মনে করা হয় তাঁর সবচেয়ে ভালো কাজ । যেভাবে চাঁদ তার আলো সূর্য থেকে পায়, ভেরলেন চাইলেন এমন বিষয়বস্তু বেছে নিতে যা সহজে অভিগম্য নয়, তাই চাঁদের মতো পরোক্ষভাবে বিষয়বস্তুকে দীপ্ত করতে চাইলেন, যা প্রতিফলন সৃষ্টি করে ।
ভেরলেনের কবিতাটিতে আছে মুখোশ আর নৃত্য, অভূতপূর্ব ছদ্মবেশ, আহ্লাদিত ঝর্ণাদের ফোঁপানি, চাঁদের আলো : বিশেষকিছু না বলেই কবিতাটিতে ইশারামূলক ছবির স্লাইড চলে যায় একের পর এক । ডেভিড ওইসত্রাখ ও ফ্রিদা বাওয়ের এই কবিতাটিকে নিয়ে একটি নৃত্যনুষ্ঠান করেছেন । ক্লদ দেবুসি, রেনাল্দো হাহন, পোলদোস্কি, গুস্তাভ কার্পেন্তিয়ের এবং গ্যাব্রিয়েল ফাওরে নিজেদের মতো করে সুর দিয়েছেন কবিতাটিতে । ইংরেজিতে যাঁরা অনুবাদ করেছেন তাঁরা বলেছেন কবিতাটি অনুবাদ করা কঠিন।
Moonlight
Your soul is like a landscape fantasy,
Where masks and Bergamasks, in charming wise,
Strum lutes and dance, just a bit sad to be
Hidden beneath their fanciful disguise.
Singing in minor mode of life's largesse
And all-victorious love, they yet seem quite
Reluctant to believe their happiness,
And their song mingles with the pale moonlight,
The calm, pale moonlight, whose sad beauty, beaming,
Sets the birds softly dreaming in the trees,
And makes the marbled fountains, gushing, streaming--
Slender jet-fountains--sob their ecstasies.
আমি এখানে শুভদীপ নায়কের করা বাংলা অনুবাদ দিলুম । উনি নামকরণ করেছেন ‘জ্যোৎস্না’
জ্যোৎস্না
( clair de lune / Moonlight)
তোমার অন্তর এক প্রশস্ত কল্পনার মতো
সেখানে মুখোশ ও মুখশ্রী দুই-ই প্রজ্জ্বলিত
বীণার তার এবং নৃত্য, যা আসলে বেদনামথিত
তোমাকে লুকিয়ে রাখে সৌন্দর্যের আড়ালে
সঙ্গীতকে ধীরে ধীরে করে তোলো বৃহৎ জীবন
ভালবাসাময়, নিশ্চল ও শান্ত
তাদের সুখের ওপর বজায় রাখো বিশ্বাস
সেইসব সঙ্গীত তুমি ধরে রাখো জ্যোৎস্নায়
শান্ত পরাভব সেই জ্যোৎস্না, অপূর্ব ক্লেশে বিকশিত
পাখিদের মতো এসে বসে স্বপ্নময় গাছের ডালে
হয়ে ওঠে ঝর্ণা, চিত্তের প্রবাহ
ঝর্ণার ঋজুতায়, -- নিজস্ব উল্লাসে
একজন মানুষের আত্মার রুপকশোভিত ছবিতে, ‘চাঁদের আলো’ জাগিয়ে তোলে সৌন্দর্য, ভালোবাসা আর প্রশান্তির আকাঙ্খা । কবিতাটি থেকে ক্রমবর্ধমান হতাশার যে আবহ গড়ে ওঠ তাতে পাওয়া যায় ভেরলেনের আত্মমগ্নতার কন্ঠস্বর । ভেরলেন পাঠকের মনে সন্দেহ তৈরি করতে চেয়েছেন, যাতে সে ভাবতে বাধ্য হয়, বাস্তবে কি সত্যিই ভালোবাসা আর আনন্দ পাওয়া সম্ভব । প্রধান উপমাটিকে প্রয়োগ করে তিনি বলতে চেয়েছেন যে প্রত্যেক মানুষই তার অন্তরজগতে একটা ভূদৃশ্য বহন করে, আর এই ক্ষেত্রে, যে উপাদান তৈরি হয় তা হলো একই সঙ্গে সুন্দর আর আশাহীন । অস্তিত্ব এবং যা দেখা যাচ্ছে, তার বৈপরীত্য কবিতাটির গুরুত্বপূর্ণ থিম । দৈহিক সৌন্দর্য আর বিষাদের মিশ্রিত অবস্হান ভেরলেন পেয়েছেন নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে । তাঁর মতে, মানুষের জীবনে এবং আত্মায়, অর্থাৎ মৃত্যুর পর, তার নিখুঁত হবার প্রয়াস কখনও পুরণ হবে না । জীবনের সত্যকার সত্তা উপরিতলে পাওয়া যাবে না ।
ভেরলেনের সযত্নে রচিত কবিতার বনেদ প্রায়শই তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতানির্ভর, নিঃসন্দেহে নাটকীয় এবং আবেগমথিত বিষয়বস্তু । তাঁর “Poemes saturniens” প্রস্তাবনায় স্পষ্ট যে তিনি নিজের অবজ্ঞাত, দৈন্যপীড়িত, দুর্দশাগ্রস্ত নিয়তি আঁচ করতে পেরেছিলেন । এই কাব্যগ্রন্হের সব কয়টি কবিতায় তিনি তুলে ধরেছেন অসুখী থাকার স্বপূরক প্রত্যাশার একাধিক বিন্যাস । আনন্দের ক্ষণিক মুহূর্ত ভেরলেনের সমস্ত কবিতায় ছেয়ে আছে । এমনকি “Sagesse” গ্রন্হে, যেখানে রোমান ক্যাথলিক রহস্যময়তার কথা বলেছেন, এবং বলেছেন যে তাতেই আছে সর্বোচ্চ আনন্দ, ঈশ্বরের সঙ্গে শান্তিময় আলাপনের সময়েও তিনি অধঃপতনের সময় ফিরে আসার ভয়ে আতঙ্কিত । যেহেতু যৌনতা, ঈশ্বর আর আবসাঁথ তাঁর ‘শনিআক্রান্ত নিয়তি’ থেকে মুক্তি দিতে পারেনি, তাই তাঁকে শেষ পর্যন্ত অন্য আশ্রয় খুঁজতে হয়েছে, এবং তা হল ঘুম । শেষ দিকের কবিতায় বারে বারে ঘুরেফিরে এসেছে ঘুমের কথা, চিত্রকল্পগুলো ঘুমের, যেন কমনীয় ঘুমপাড়ানি গানের মনোরম ছবি -- তা থেকে রঙ, হাসি, তীক্ষ্ণতা, জমকালো, মাত্রাধিক ধ্বনি বাদ দেয়া হয়েছে -- কবির ক্ষতবিক্ষত মনকে ঘুমের আরামে শান্তি দিতে পারে । বেশ কিছু কবিতায় এক মাতৃমূর্তিকে পাওয়া যায় দোলনার পাশে কিংবা এক মাতৃমূর্তি লক্ষ রাখেন ঘুমন্ত কবির পাশে দাঁড়িয়ে । যে কবিতায় ঘুমের মোটিফ নেই, তাতেও কবিতার শেষের পঙক্তিগুলোয় এসেছে মুছে যাবার রিক্ততাবোধ ।
আলোচকরা ভেরলেনকে তাঁর কবিতার শিল্পানুগ ও গভীর অনুভূতির বৈশিষ্ট্যের কারণে ফরাসী প্রতীকবাদের অগ্রদূতদের একজন হিসাবে চিহ্ণিত করলেও, তিনি তাঁর কবিতাকে ডেকাডেন্ট বা প্রতীকবাদের তকমা দিতে অস্বীকার করে বলেছেন যে তিনি নিজেকে একজন ‘ডিজেনারেট’ বা অপজাত কবি বলতে চাইবেন, কেননা তাঁর কবিতায় থাকে অহংকার ও অরাজকতার প্রবণতা ; প্রতীকবাদীদের তুলনায় তিনি প্রচলিত ভাষাকে সঙ্গীতময় করেছেন তাঁর কবিতায়। প্রকৃতপক্ষে ভেরলেনের জীবনের ঘটনাবলী ছেয়ে ফেলেছে তাঁর কবিতার গুণাগুণ ও কাব্যিক প্রতিভা । যেমন তাঁর জীবনে, তেমনই তাঁর কবিতায়, অবিরম লড়াই দেখা যায় তাঁর অন্তরজগতের সঙ্গে তাঁর ইন্দ্রিয়ের, লাম্পট্য ও পশ্চাত্যাপের । তাঁর চরিত্রকে আক্রমণ সত্বেও, ভেরলেনকে মনে করা হয় একজন সুসম্পূর্ণ কবি, যাঁর অসাধারণ প্রতিভা দেখা যায় কবিতার অঘনিভূত মাত্রায়, ইশারামূলক ও লাক্ষণিক ভাষায় এবং প্রতিচ্ছায়াময় বাক্যালঙ্কারে । ফরাসি কবিতাকে ভেরলেনই পরিভাষাগত প্রাবল্যের বাইরে বের করে আনেন এবং ফরাসী ভাষার সহজাত সঙ্গীতময়তাকে ব্যবহার করা আরম্ভ করেন । তিনি বলেছেন কবিতা হওয়া উচিত সুখশ্রাব্য ও সন্মোহক, অস্পষ্ট ও দ্রবনীয় ; পাঠক কবিতাকে বিভিন্ন থিমে চিহ্ণিত করতে পারবেন, এমন কবিতা লেখা তিনি পছন্দ করেন না । সেকারণেই তাঁর কবিতার অনুবাদে তাঁকে সম্পূর্ণ পাওয়া যায় না। তাঁর বক্তব্য বোঝাবার জন্য ভেরলেন কবিতার শিল্প (Art Poetique ) শিরোনামে একটি কবিতা লিখেছিলেন ; আমি বাংলায়নের চেষ্টা করেছি :
সবকিছুর আগে সঙ্গীতময়তা--
আর এর জন্য আরও অস্বাভাবিকতা--
অস্পষ্ট ও আরও বেশি বাতাসে মিলিয়ে যাওয়া,
তাকে ভার বইতে হয় বা বেঁধে ফেলতে হয় তাকে বাদ দিয়ে দাও
তাকে এমন হতে হবে যে তুমি খুঁজে বেড়াবে
তোমার শব্দগুলোয় কোনোরকম গাফিলতি ছাড়াই :
ধূসর গান ছাড়া প্রিয় আর কিছু নেই
যেখানে বিচলন ও যথাযথের মিল হয় ।
আনেকটা কালোজালের আড়ালে সুন্দর চোখের মতন,
অনেকটা ছড়িয়ে-পড়া দুপুরের স্পন্দনের মতন,
অনেকটা ( যখন হেমন্তের আকাশ শোভনীয় করে তোলে )
সুস্পষ্ট নক্ষত্রদের নীল বিশৃঙ্খলা !
কেননা আমরা আরও বেশি চাই সূক্ষ্ম তারতম্য--
রঙ নয়, সূক্ষ্ম তারতম্য ছাড়া কিছু নয় !
ওহ ! কেবল সূক্ষ্ম তারতম্য নিয়ে আসে
স্বপ্নকে স্বপ্নের মধ্যে আর বাঁশিকে শিঙায় !
খুনির ধারালো বক্তব্য থেকে দূরে রাখো,
নিষ্ঠুর বৈদগ্ধ আর পঙ্কিল হাসি,
যা নীল শূন্যতার চোখে অশ্রূজল এনে দ্যায়---
আর মৃদু আঁচের যাবতীয় রসুনরান্না ।
বাগ্মীতাকে ধরে তার ঘাড় মুচড়ে দাও !
তোমার তাতে ভালো হবে, কর্মচঞ্চল মেজাজে,
যাতে কবিতার মিলকে কিছুটা সুবিচার করা যায় ।
যদি না লক্ষ রাখা হয়, তাহলে তা কোথায় যাবে ?
ওহ, কে আমাদের বলতে পারে মিলের ভ্রষ্ট আচরণ ?
কোন বধির বালক কিংবা উন্মাদ কালো মানুষ
আমাদের জন্য বানিয়েছে এই এক পয়সার খেলনা,
যা ফাঁপা শোনায় আর শুনে মনে হয় নকল
সঙ্গীতকে হয়ে উঠতে দাও, অনেক বেশি করে আর সবসময় !
তোমার কবিতা হয়ে উঠুক চলমান জিনিস
যাকে অনুভব করে মনে হবে তা বদলে যাওয়া আত্মা থেকে পালিয়ে যাচ্ছে,
অন্য আকাশ থেকে অন্য প্রেমের দিকে ।
তোমার কবিতাকে আনন্দময় ঘটনা হয়ে উঠতে দাও,
অস্হির ভোরের বাতাসের মাঝে,
যা পুদিনা আর থাইমলতার সুগন্ধ নিয়ে উড়ে বেড়ায়…
আর বাদবাকি সমস্তই সাহিত্য ।
ফ্রান্সে, রোমান্টিসিজমের পর, তখন রোমান্টিসিজম বলতে যা বোঝাতো, আর পারনাসিয়দের দ্ব্যর্থহীন, ধ্রুপদি, অতিরিক্ত যত্নবান, চিত্তাকর্ষকভাবে মোহনীয় কবিতার যুগের পর, সমাজ যখন কলকারাখানার আধুনিকতাবাদী সমাজে অনিশ্চিত জীবনযাপনের মুখোমুখি হওয়া আরম্ভ করল, গ্রাম থেকে দলে-দলে পরিবার শহরে অনিশ্চিত জীবনধারায় বসবাস করতে আরম্ভ করল,তখন পল ভেরলেনের মতন কবিরা কবিতায় অনিশ্চয়তার ও অনির্ণেয়তার প্রয়োজন অনুভব করলেন । পল ভেরলেনের ‘আর্ট পোয়েটিক’ কবিতাটি বাস্তব জীবনে অনিশ্চয়তার উপস্হিতিকে কবিতায় আনতে চেয়েছে । তিনি অনুভব করলেন যে মানুষ চায় না তাকে সীমা দিয়ে বেঁধে রাখা হোক, সে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থাকতে চায় । নিজের বিবাহিত জীবন এবং পায়ুকামীদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ও কারাগারের জীবন থেকে তেমনটাই তাঁর মনে হয়ে থাকবে । ১৮৭৪ সালে যখন তিনি বললেন, ‘প্রথম এবং সর্বাগ্রে সঙ্গীত’, তখন ফরাসি কবিতায় নতুন কিছুর কথা বললেন তিনি । ফরাসি কবিতা চিরকালই সঙ্গীতময় ছিল, কিন্তু ভেরলেনের আগে কেউ বলেননি যে সঙ্গীতই কবিতায় মূল ব্যাপার । তার আগে তো ছিলই উপলবব্ধির গভীরতা, দৃষ্টিলব্ধ অবধারণা, বাচনিক নমনীয়তা ও পারিপাট্য । ভেরলেন সঙ্গীতকে কবিতায় গৌরবান্বিত করলেন । কবিতায় সঙ্গীত অদেখা বাস্তবতা সম্পর্কে যথাযথ হবার উপায় বাতলায় এবং যে বাস্তবতা স্পষ্টভাবে প্রভাবান্বিত করে তাকে কবিতার সিংহাসনে বসায় ।
চার
পল ভেরলেন আদেনেস থেকে জাঁ আর্তুর র্যাঁবো নামে সতেরো বছরের এক কবিযশোপ্রার্থীর চিঠি আর চিঠির সঙ্গে তার লেখা কয়েকটি কবিতা পড়ে মুগ্ধ হলেন, আর তাকে গাড়িভাড়া পাঠিয়ে বললেন প্যারিসে চলে আসতে । ১৮৭১ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর শার্লভিল থেকে প্যারিস পৌঁছোলেন র্যাঁবো, সঙ্গে নিজের পাণ্ডুলিপি নিয়ে, যার মধ্যে একটি কবিতার শিরোনাম ছিল, ‘দি ড্রাঙ্কেন বোট’ বা ‘মত্ত নৌকো’ । স্টেশনে কেউ ছিল না তাঁকে আপ্যায়ন করার জন্য। ভেরলেন, তাঁর বন্ধু শার্ল গ্রস্ত-এর সঙ্গে গার দু নর্দ আর গার্দ দ্যলেস্ত-এর মাঝে দৌড়ঝাঁপ করছিলেন তরুণ অতিথির জন্য । শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে মমার্ততে মাতিলদের বাবা-মায়ের বাড়ি ফেরার পথ ধরলেন ; পল ভেরলেন বিয়ের পর শশুরবাড়িতে থাকতেন । পথে তাঁরা খুঁজে পেলেন রোদে পোড়া গম্ভীর-মুখ, নীল চোখ, তরুণটিকে, যে, তাঁদের সঙ্গে আরদেনেসের বাচনভঙ্গীতে হ্যাঁ-হুঁ করে সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়ে কথা বলল ।
বারো বছর পরে তাঁর স্মৃতিচারণে ভেরলেন লিখেছেন যে, “তরুণটি ছিল দীর্ঘ, শক্ত কাঠামোর, খেলোয়াড়দের মতো আদরা, নিখুঁত ডিম্বাকার মুখ, যেন নির্বাসন থেকে ফেরা এক দেবদূত ; দেহের শক্ত কাঠামোর ওপরে শিশুসূলভ গালফোলা মুখ, হাবভাবে বয়ঃসন্ধি কাটিয়ে দ্রুত বেড়ে-ওঠা জবুথবুপনা ।” ভেরলেনের স্ত্রী আর শাশুড়ি তরুণটিকে বাড়িতে নিয়ে আসা যে ভালো হয়নি তা স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, কিন্তু তাড়াতে পারলেন না কেননা ভেরলেনের শশুর সেসময়ে বন্ধুদের সঙ্গে শিকারে গিয়েছিলেন । এক দিনেই তাঁরা টের পেলেন যে অতিথিটি চাষাড়ে, বাড়ির বাইরে বেরিয়ে উলঙ্গ হয়ে রোদ পোয়ায়, যে ঘরে থাকতে দেয়া হয়েছিল তাকে করে ফেলেছে নোংরা আর লণ্ডভণ্ড, যিশুর ছোটো ক্রস ভেঙে ফেলেছে, চুলে উকুন । ভেরলেন যা করতে চাইতেন অথচ করার সাহস পেতেন না, অতিথিকে সেসব করতে দেখে পুলক বোধ করছিলেন ।
অতিথিকে বন্ধুদের আড্ডায় নিয়ে গেলেন ভেরলেন । লিয়ঁ ভালাদে নামে ভেরলেনের এক বন্ধু তাঁর আরেক বন্ধুকে লিখে জানিয়েছিলেন, “তুমি পল ভেরলেনের নতুন আবিষ্কারের সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ পেলে না, ভেরলেন যে তরুণটির জন দ্য ব্যাপটিস্ট ; বড়ো-বড়ো হাতের চেটো, বড়ো-বড়ো পা, মুখ যেন তেরো বছরের বাচ্চার, চোখ দুটো নীল, আর তরুণটি ভিতু মনে হলেও, মতামত অসামাজিক মনে হলো, কল্পনাশক্তি অজানা কুকর্মে ঠাশা, বন্ধুরা তো সবাই তাকে দেখে একই সঙ্গে মুগ্ধ আর আতঙ্কিত । তরুণটি যেন ডাক্তারদের মাঝে একজন শয়তান ।” প্রকাশক গঁকুরভাইদের একজন জানিয়েছেন যে ভেরলেনের অতিথির সঙ্গে হাত মিলিয়ে মনে হচ্ছিল সবচেয়ে বজ্জাত কোনো খুনির হাত ।
মাতিলদের বাবার ফেরার আগের দিন ভেরলেনের অতিথিকে নিজের বাড়িতে কয়েকদিন রাখলেন শার্ল ক্রস ; তারপর পারনাসিয় কবি থিয়োদোর দ্যবাঁভিলের বাড়িতে চাকরানির ঘরে স্হান পেলেন । প্রথম রাতে জানলা দিয়ে নিজের ভিজে জামা-কাপড় রাস্তায় ছুঁড়ে-ছুঁড়ে ফেললেন তরুণটি, চিনামাটির বাসন ভেঙে ফেললেন, বিছানায় কাদামাখা জুতো পরে শুলেন, আর গোপনে কয়েকটা আসবাব বেচে দিলেন । বাঁভিলও এক সপ্তাহ কাটতেই ভেরলেনকে বললেন নিজের অতিথিকে ফেরত নিয়ে যেতে । তরুণটির আচরণে একমাত্র ভেরলেনই আহ্লাদিত হচ্ছিলেন । মাতিলদেকে নিয়ে কবিতাগুলো লেখার পর ভেরলেন নতুন কবিতা লেখার সময় পাননি। তরুণটি তাঁকে ওসকাচ্ছিলেন অনভিজাতের মতো জীবন কাটাতে এবং মদে চুর হয়ে দ্রষ্টার মতো কবিতা লিখতে । তাছাড়া পল ভেরলেন পেয়ে গিয়েছিলেন তাঁর পায়ুকামের আদর্শ সঙ্গী, যাকে এক বন্ধুর বাড়ি থেকে আরেক বন্ধুর বাড়িতে রক্ষিতার মতন লুকিয়ে রাখতে হচ্ছিল। ভেরলেন তাঁর অভিজাত পোশাক ছেড়ে নামানো-টুপি আর গলায় মাফলার ধরেছিলেন, অতিথির জন্য টাকাকড়ি খরচ করছিলেন প্রচুর । তাঁদের পায়ুকামের সম্পর্ক যখন আর গোপন রইলো না তখন ভেরলেনের বন্ধুরা তাঁর পাশ থেকে সরে যেতে লাগলেন । দুজনে মিলে গুহ্যদ্বার নিয়ে একটা সনেট লিখলেন ( Sonnet du trou cul ), যার প্রথম আট লাইন ভেরলেনের এবং পরের ছয় লাইন র্যাঁবোর । কবিতাটা ফরাসি থেকে ইংরেজিতে অনেকে অনুবাদ করেছেন ; আমি পল শ্মিট-এর অনুবাদটা দিলুম এখানে :
Hidden and wrinkled like a budding violet
It breathes, gently worn out, in a tangled vine
(Still damp with love), on the soft incline
Of white buttocks to the rim of the pit.
Thin streams like rivers of milk ; innocent
Tears, shed beneath hot breath that drives them down
Across small clots of rich soil, reddish brown,
Where they lose themselves in the dark descent…
My mouth always dribbles with its coupling force;
My soul, jealous of the body's intercourse,
Makes it tearful, wild necessity.
Ecstatic olive branch, the flute one blows,
The tube where heavenly praline flows,
Promised Land in sticky femininity.
র্যাঁবোকে একই সঙ্গে চরস আর আবসাঁথ খাইয়ে ভেরলেন অতিথিকে পরিচয় করিয়ে দিলেন নতুন অভিজ্ঞতার সঙ্গে, যার অন্বেষণ করছিলেন তিনি, ‘ইন্দ্রিয়গুলোর অপরিমেয় ও নিয়মানুগ বিশৃঙ্খলা’ ঘটানোর জন্য । ২১ অক্টোবর ১৮৭১ ভেরলেনের ছেলের জন্ম হলো এবং সংবাদটিতে আনন্দিত হবার বদলে ক্রুদ্ধ হলেন তিনি । মাতিলদে জানিয়েছেন যে অক্টোবর ১৮৭১ থেকে জানুয়ারি ১৯৭২ পর্যন্ত ভেরলেন তাঁকে মারধর করতেন আর খুন করার হুমকি দিতেন, একদিন সত্যিই গলা টিপে ধরেছিলেন, হাতখরচ না পেয়ে । স্বামীর দুর্ব্যাবহার আর মা-বাবার কাছে লুকোতে পারলেন না মাতিলদে, কেননা মাতিলদের দেহে আঘাতের চিহ্ণ আর স্বামীর কথা জিগ্যেস করলেই তাঁর কান্না থেকে তাঁরা বুঝে গিয়েছিলেন জাঁ আর্তুর র্যাঁবো নামে চাষার ছেলেটা আসার পরে কি ঘটছে মেয়ের শোবার ঘরে । জামাইয়ের পায়ুকামের প্রতি আকর্ষণের খবরও তাঁদের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল । ডাক্তার ডেকে মাতিলদেকে পরীক্ষা করিয়ে মেয়ে আর মেয়ের ছেলেকে পাঠিয়ে দিলেন তাঁদের পারিবারিক বাড়ি পেরিজিউতে ।
স্ত্রী চলে যাবার পর ভেরলেন বিয়েটা বাঁচানোর চেষ্টায় র্যাঁবোকে বললেন বাড়ি ফিরে যেতে ; সবকিছু ঠাণ্ডা হয়ে গেলে দুজনে আবার একত্রিত হতে পারবেন । প্যারিসে আসার ছয় মাস পরে মার্চ ১৮৭২ সালে বাড়িমুখো হলেন র্যাঁবো ; তিনি জানতেন যে তাঁকে ছাড়া ভেরলেনের চলবে না । মাতিলদে ছেলেকে নিয়ে প্যারিসে ফিরলেন, তাঁর মনে হলো মিটমাট হয়ে গেছে, চাষার ছেলেটা বিদেয় হয়েছে । ভেরলেনও চাকরি খুঁজতে লাগলেন । কিন্তু গোপনে চিঠি লিখতে লাগলেন র্যাঁবোকে, জানতে চাইলেন কেমন করে কোথায় দুজনে মিলিত হবেন । পায়ুকামর নেশায় ভেরলেনের কবিতা থেকে মিনার্ভা আর ভিনাস বিদায় নিয়েছিলেন । র্যাঁবোর প্রভাবে ভেরলেন তাঁর অন্তরজগতে লুকিয়ে থাকা দানবটাকে বাইরে বের করে আনার সুযোগ পেয়ে গেলেন । ভেরলেনের দানবকে সহ্য করতে না পেরে ১৮৭২ সালে মেয়ের সঙ্গে আইনি বিবাহবিচ্ছেদের অনুমতি দিলেন মাতিলদের বাবা, তখনও ডিভোর্স প্রচলিত হয়নি । ১৮৮৪ সালে ডিভোর্স আইনসঙ্গত হলে মাতিলদের সঙ্গে ভেরলেনের ডিভোর্স হয় । মাতিলদে আবার বিয়ে করেছিলেন এবং একষট্টি বছর বয়সে মারা যান ।
১৮৭২ সালের সেপ্টেম্বরে ভেরলেন আর র্যাঁবো লণ্ডন পৌঁছোলেন ; সেইসময়ে লণ্ডন ও বিশেষ করে সোহো ছিল ফরাসি কমিউনের পলাতক সদস্যদের লুকোবার পক্ষে ভালো জায়গা । কমিউনের প্রতি ভেরলেনের আগ্রহ থাকলেও র্যাঁবোর ছিল না । ভেরলেনকে তাঁর বুর্জোয়া মানসিক গঠন থেকে মুক্তি দেবার জন্য র্যাঁবো তাঁকে উৎসাহিত করলেন মুসেত এবং লেকঁত দ্যলিজের কবিতা পড়তে, ফরাসি কবিতার বারো মাত্রার ঐতিহ্য এবং ব্যালাডের আট মাত্রা অনুসরণ না করে দশ মাত্রার কবিতা লিখতে । র্যাঁবো তাঁকে পরামর্শ দিলেন কবিতা থেকে মানবিক কাহিনি, বাস্তববাদী ছবি আর ভাবপ্রবণ প্রতিকৃতি বাদ দিতে । পল ভেরলেনের মতে র্যাঁবোর ভালো লেগেছিল লণ্ডন ; তিনি ভেরলেনকে বলেছিলেন যে লণ্ডনের তুলনায় প্যারিসকে শহরতলি মনে হয়, লণ্ডনে রয়েছে কয়লা-চালিত ফ্যাক্ট্রি, টেমস নদীর ধারে জাহাজের ডক এবং সর্বোপরি একটি সাম্রাজ্যের রমরমা। ভেরলেন সেসমস্ত ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন না, তিনি কেবল কচি-তরুণ র্যাঁবোর সঙ্গে দৈহিক মিলনেই বেশি আনন্দ পেতেন, লণ্ডনে তাঁদের যথেচ্ছাচারে বাধা দেবার কেউ ছিল না । র্যাঁবোর ‘নরকে এক ঋতু’ কবিতার ‘ফুলিশ ভার্জিন’ প্রসঙ্গ ভেরলেন সম্পর্কে । তাঁরা ডেরা নিয়েছিলেন কামডেনের গ্রেট কলেজ স্ট্রিটে ( এখন রয়াল কলেজ স্ট্রিট ); বাড়িটিতে একটা প্লেট লাগানো আছে যে তাঁরা দুজনে সেখানে ছিলেন । নিজেদের ‘উৎকট দম্পতি’ হিসাবে উল্লেখ করেছেন র্যাঁবো । লণ্ডন থেকে প্যারিসে এক বন্ধুকে ভেরলেন লিখেছিলেন যে, “আমি আর ফরাসি সংবাদপত্র পড়িনা ; পড়ে হবেই বা কি?” তাঁরা দুজনে ব্রিটিশ মিউজিয়ামের গ্রন্হাগারে যেতেন বটে কিন্তু পল ভেরলেন যেতেন শহরের শীত থেকে বাঁচার জন্য, যখন কিনা র্যাঁবো যেতেন বিনে পয়সায় কাগজ-কলম-কালি পাওয়া যেতো বলে। বইপত্র পড়তেন । লণ্ডনের বাইরে বেড়াতে যেতেন দুজনে, ভেরলেন হ্যাম্পস্টেড হিথের কথা লিখেছেন, গ্রামাঞ্চল দেখার জন্য । র্যাঁবোকে ছাড়তে না পারার কারণ হিসাবে ভেরলেন লিখেছেন যে, এক ধরণের মিষ্টতা ঝলকাতো ওর নিষ্ঠুর ফিকে-নীল চোখে আর লালচে ঠোঁটের কটু ইশারায় । ইতিমধ্যে র্যাঁবো তাঁর বিখ্যাত কবিতা ‘মত্ত নৌকো’র আঙ্গিক ছেড়ে নতুন ধরণের গদ্য-কবিতার দিকে ঝুঁকছিলেন, যার পরিচয় পাওয়া যাবে তাঁর ‘নরকে এক ঋতু’ আর ‘ইল্যুমিনেশান্স’-এর কবিতাগুলোতে ।
লণ্ডন তাঁদের দুজনকেই অবাক করেছিল, আহ্লাদিত করেছিল । ভেরলেন বিস্মিত হয়েছিলেন দিগন্ত পর্যন্ত চলে যাওয়া রেলপথ আর লোহার সেতু দেখে, আর পথে-পথে নির্দয়, বারফট্টাই-মারা জনগণকে দেখে । ভেরলেন লিখেছেন লণ্ডন ছিল অতিশালীন, কিন্তু অসচ্চরিত্র হবার সব রকমের সুযোগ ছিল অবারিত, আর প্রচুর খরচ সত্বেও, তাঁরা সদাসর্বদা থাকতেন এইল, জিন আর আবসাঁথে মাতাল । আবসাঁথের সবুজ পরী র্যাঁবোকে ডাক দিয়েছিল ‘স্বরবর্ণ’ নামের কবিতাটি লিখতে ।
স্বরবর্ণ
A কালো, E শাদা, I লাল, U সবুজ, O নীল : স্বরবর্ণ
কোনো দিন আমি তোমার জন্মাবার কান্না নিয়ে কথা বলবো,
A, মাছিদের উজ্বল কালো মখমল জ্যাকেট
যারা নিষ্ঠুর দুর্গন্ধের চারিধারে ভন ভন করে,
ছায়ার গভীর খাত : E, কুয়াশার, তাঁবুগুলোর অকপটতা,
গর্বিত হিমবাহের, শ্বেত রাজাদের বর্শা, সুগন্ধলতার শিহরণ :
I, ময়ূরপঙ্খীবর্ণ, রক্তাক্ত লালা, নিঃসঙ্গের হাসি
যার ঠোঁটে ক্রোধ কিংবা অনুশোচনায় মাতাল :
U, তরঙ্গ, ভাইরিডিয়ান সমুদ্রের দিব্য কম্পন,
চারণভূমির শান্তি, গবাদিপশুতে ভরা, হলরেখার শান্তি
কিমিতির চওড়া পড়ুয়া ভ্রুজোড়া দিয়ে বিরচিত :
O, চরম তূর্যনিনাদ, অদ্ভুত কর্কশ আওয়াজে ভরপুর,
জগত আর দেবদূতে রেখিত নৈঃশব্দ :
O, সমাপ্তি, মেয়েটির চোখের বেগুনি রশ্মি !
র্যাঁবো খ্রিসমাসের জন্য বাড়ি ফিরলেও ভেরলেন ফিরতেন না ;র্যাঁবোর সমস্যা ছিল মা সবসময় বলতেন একটা চাকরি খুঁজে জীবনে স্হির হতে । ভেরলেন পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন সংসারের বাঁধন থেকে, দায়িত্ব থেকে, এবং পাপবোধে ভুগে কাঁদতেন মাঝেমধ্যে ; তাঁর কাছে র্যাঁবো ছিলেন ‘দীপ্তিময় পাপ’ আর র্যাঁবোর কাছে ভেরলেন ছিল ‘ক্ষুদে প্রিয়তমা’ । ইংরেজি শব্দের তালিকা তৈরি করেছিলেন এবং লণ্ডনে চাকরি খুঁজতে আরম্ভ করেছিলেন ভেরলেন। ফ্রান্সের গোয়েন্দা প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে পল ভেরলেনের ওপর লক্ষ রাখা হচ্ছিল। তাঁর ভবিষ্যতের জীবনীকার এদমন্দ লেপেলেতিয়েকে ভেরলেন লিখেছিলেন যে, “আশা করছি কয়েক দিনের মধ্যেই একটা বড়ো সংস্হায় চাকরি পাবো, যেখানে প্রচুর রোজগার করা যাবে, ইতিমধ্যে আমি কয়েকটা আমেরিকান সংবাদপত্রের জন্য কাজ করছি যারা ভালো পয়সাকড়ি দ্যায় ।” লেপেলেতিয়ে তার কোনো প্রমাণ পাননি, এবং সবই ভেরলেনের বানানো, ফরাসি কবিদের ঈর্শ্বান্বিত করার জন্য । দুজন ভবঘুরে লণ্ডনের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন কাজের জন্য কিন্তু কারোর সাড়া তাঁরা পাননি । লেপেলেতিয়ে একটা কাগজের বিজ্ঞাপন জোগাড় করতে পেরেছিলেন, সম্ভবত র্যাঁবোর তৈরি খসড়া :
এক ফরাসি ভদ্রলোক ( ২৫ ), অভিজাত সমাজে যাঁর ভালো যোগাযোগ আছে, উচ্চশিক্ষিত, ফরাসি ডিপ্লোমাধারী, ইংরেজিতে সড়গড়, এবং বিপুল সাধারণ জ্ঞানের মানুষ, ব্যক্তিগত সচিব, পর্যটনের সঙ্গী কিংবা গৃহশিক্ষকের চাকরি খুঁজছেন । সম্ভ্রান্তদের সুপারিশ আছে । ঠিকানা : ২৫ ল্যানঘাম স্ট্রিট ।
র্যাঁবোর ‘ইল্যুমিনেশান্স’-এর ‘ভবঘুরে’ কবিতাটি ( ১৮ নং ইল্যুমিনেশান ) তাঁদের দুজনের সেই সময়টিকে ধরে রেখেছে :
সমব্যথী ভাই ! ওর কাছে আমার কোনও নৃশংস নিশিপালন আছে ! ‘আমি এই ঝুঁকিপূর্ণ কর্মপ্রচেষ্টাকে দখল করে নিতে বিফল হয়েছিলুম । আমি ওর অকর্মণ্যতা নিয়ে ঠাট্টা করেছিলুম । যদি আমাদের নির্বাসনে যেতে হয়, কেনা-গোলমী করতে হয়, তা হবে আমার দোষ।’ অদ্ভুত দুর্ভাগ্য আর বোকামির জন্য ও আমার প্রশংসা করেছিল, আর তার সঙ্গে জুড়েছিল অশান্তিকর কারণ ।
এই শয়তান পণ্ডিতকে আমি বিদ্রুপ করে উত্তর দিয়েছি, আর জানালার কাছে গিয়ে তা শেষ করেছি । বিরল সঙ্গীতরেখার চালচলনের অপর পারের চারণভূমিতে আমি ভবিষ্যতের রাতের বিলাসের মায়াপুরুষ গড়েছি ।
এই অস্পষ্ট স্বাস্হবিধিসন্মত চিত্তবিক্ষেপের পর, আমি খড়ের মাদুরের ওপরে হাতপা ছড়িয়ে শুয়ে পড়তুম । এবং, বলতে গেলে প্রতি রাতে, যেই আমি ঘুমিয়ে পড়তুম, বেচারা ভাইটি উঠে পড়তো, মুখে দুর্গন্ধ, চোখে দেখতে পাচ্ছে না -- যেমন ও নিজের সম্পর্কে স্বপ্ন দেখতো -- আর নিজের নির্বোধ কান্নার স্বপ্নে বিভোর আমাকে ঘরের ভেতরে টানাটানি করতো !
বাস্তবিক, সত্যি বলতে কি, আমি ওকে ওর সূর্যসন্তানের প্রাগৈতিহাসিক স্হতিতে ফিরিয়ে আনার প্রতিজ্ঞা করেছিলুম -- আর আমরা ঘুরে বেড়ালুম, গুহার মদে ভরণপোষণ করে, আর পথের বিসকিট খেয়ে, আমি পরিসর আর ফরমুলা খুঁজে পাবার জন্যে অধৈর্য ।
তাঁদের দুজনের ঝগড়া গ্রেট কলেজ স্ট্রিটেই আরম্ভ হয়েছিল । তাঁদের সম্পর্ক তিক্ত হয়ে উঠেছিল । র্যাঁবো মাঝে একদিন ছুরি দিয়ে ভেরলেনের উরুতে আঘাত করেছিলেন । প্রেমিকের আঘাতের আদর বলে মেনে নিয়ে কাউকে জানাননি ভেরলেন । এই বিষয়ে ভেরলেন লিখেছেন, “আমি বাড়ি ফেরার সময়ে দেখলুম জানলা দিয়ে র্যাঁবো আমায় দেখছে । অকারেণেও আমাকে দেখে অপমানজনক ঠাট্টা-ইয়ার্কি করতে লাগলো। যাহোক আমি সিঁড়ি দিয়ে উঠলুম আর ঘরে ঢুকলুম । ‘তোমার কি কোনো ধারণা আছে এক হাতে একবোতল তেল আর অন্য হাতে একটা মাছ ঝুলিয়ে কেমন দেখাচ্ছিল তোমায় ?’ বলল র্যাঁবো । আমি তার জবাবে বললুম, আমি তোমাকে জোর দিয়ে বলতে পারি, আমাকে মোটেই উপহাসাস্পদ দেখায়নি ।’ ভেরলেন মাছটা দিয়ে র্যাঁবোর মুখে সপাটে মারলেন আর জানালেন যে তিনি আত্মহত্যা করে নেবেন । ভেরলেন চটে গিয়ে জাহাজ ধরে সোজা চলে গেলেন বেলজিয়াম, স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক জোড়া লাগাবার উদ্দেশে । সেখানে মাতিলদে ছিলেন ।
র্যাঁবো কিছুক্ষণ পরেই ডকে পৌঁছে টের পেলেন যে ভেরলেন, তাঁর ‘বুড়ি শূকরী’ , সত্যিই চলে গেছেন । নিষ্কপর্দক র্যাঁবোকে সাহায্য করার কেউ ছিল না, আর যারা ছিল তারা দুজনের দৈহিক সম্পর্ক জানতে পেরে নিজেদের দূরে সরিয়ে নিয়েছিল । র্যাঁবো ভেরলেনকে চিঠি দিলেন :
তুমি কি মনে করো যে আমার বদলে অন্য লোকেদের সঙ্গে থাকলে তুমি আনন্দে থাকবে ? ভেবে দ্যাখো ! নিশ্চয়ই না ! আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে ভবিষ্যতে আমি তোমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করব । আমি তোমাকে অত্যন্ত ভালোবাসি, আর তুমি যদি ফিরতে না চাও, কিংবা আমি তোমার কাছে যাই তা না চাও, তুমি একটা অপরাধ করছ, আর তার জন্য তুমি সমস্ত স্বাধীনতা হারিয়ে বহুকাল আফশোষ করবে, আর এতো ভয়ঙ্কর দুঃখদুর্দশায় ভুগবে যার অভিজ্ঞতা তোমার কখনও হয়নি ।
১৮৭৩ সালের ৮ জুলাই র্যাঁবোকে টেলিগ্রাম করলেন ভেরলেন ব্রুসেলসের হোটেল লিজে পৌঁছোতে । ভেরলেনের জামাকাপড় বেচে র্যাঁবো পৌঁছোলেন বেলজিয়ামের হোটেলে যেখানে ভেরলেন ছিলেন । দুজনের মনের মিল হল না, টানা কথা কাটাকাটি চলল । ভেরলেন একের পর এক আবসাঁথের বোতল খালি করে মাতাল হয়ে থাকতে চাইলেন । ১০ জুলাই তিনি একটা রিভলভার আর গুলি কিনলেন, আত্মহত্যা করবেন ভেবে । চারটে নাগাদ মাতাল অবস্হায় দুটো গুলি চালালেন র্যাঁবোকে লক্ষ করে । একটা গুলি লক্ষভ্রষ্ট হল, অন্যটা লাগল র্যাঁবোর কনুইতে । আঘাতকে বিশেষ গুরুত্ব না দিয়ে সঁ-জাঁ হাসপাতালে ড্রেসিং করিয়ে ব্রুসেলস ছাড়ার কথা ভাবলেন র্যাঁবো । সন্ধ্যা আটটা নাগাদ র্যাঁবোকে গারে দু মিদি রেলস্টেশনে ছেড়ে দেবার জন্য ভেরলেন আর ভেরলেনের মা গেলেন । আদালতে র্যাঁবোর সাক্ষ্য অনুযায়ী ভেরলেন পাগলের মতো আচরণ করছিলেন আর তাঁর পকেটে পিস্তলও ছিল । র্যাঁবো পুলিশের একজন টহলদারকে দেখতে পেয়ে দৌড়ে তার কাছে গিয়ে বললেন তাঁকে ভেরলেনের থেকে বাঁচাতে । ভেরলেন গ্রেপ্তার হলেন, তাঁর বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টার অভিযোগ উঠল, আদালতে তাঁদের দুজনের সম্পর্ক নিয়ে উকিল আর ডাক্তারদের প্রশ্নের মুখে পড়লেন ভেরলেন ।
১৭ জুলাই র্যাঁবোর বুলেট বের করার পর তিনি নালিশ তুলে নিলেন । পুলিশকে দেয়া বয়ানে র্যাঁবো লিখেছিলেন যে, গুলি চালিয়েই ভেরলেন তাঁর অপরাধের জন্য তক্ষুনি ক্ষমা চেয়ে নিলেন । পিস্তলটা আমার হাতে দিয়ে বললেন তাঁর কপাল লক্ষ করে গুলি চালাতে। তাঁর আচরণ ছিল গভীর অনুতাপের । ভেরলেনের বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টার অভিযোগ তুলে নিয়ে কেবল আঘাত করার অভিযোগ বজায় রইলো । তাঁদের পরস্পরের পায়ুকাম নিয়ে আদালতে অপমানজনক কথাবার্তা হলেও তাকে অপরাধ বলে মনে করা হয়নি এবং পুলিশ আরোপ করেনি । ৮ই আগস্ট ১৮৭৩ ভেরলেনের দুই বছরের কারাদণ্ডের আদেশ হল ।
র্যাঁবো শার্লভিল ফিরে গিয়ে ‘নরকে এক ঋতু’ লেখা শেষ করলেন । তাতে ভেরলেনকে তিনি ‘উন্মাদিনী ভার্জিন’ হিসাবে উল্লেখ করেছেন, আর নিজেকে ‘নারকীয় স্বামী’ হিসাবে আর তাঁদের একসঙ্গে বসবাসকে বলেছেন ‘গার্হস্হ প্রহসন’। ১৮৭৪ সালে র্যাঁবো ফিরেছিলেন লণ্ডনে, কবি জারমেইন নোভোর সঙ্গে, তিন মাস ছিলেন একসঙ্গে । এই সময়ে তিনি ‘ইল্যুমিনেশান্স’-এর গদ্য-কবিতাগুলো লেখা শেষ করেন । কিন্তু পায়ুকামের নায়ক-নায়িকা বা আদম-ইভের কাহিনি এখানেই ফুরোয়নি । জেল থেকে র্যাঁবোকে চিঠি লিখতেন আর নিজের নতুন লেখা কবিতা পাঠাতেন, যেগুলো পড়ে র্যাঁবো মোটেই উৎসাহিত হতেন না । র্যাঁবো তখন কবিতা ও সাহিত্যজগত সম্পর্কে উদাসীন এবং নতুন জীবনের সন্ধান করেছেন, বাবার মতো উধাও হয়ে যেতে চাইছেন । পরস্পরের দৈহিক ভালোবাসার বদলে যিশুখ্রিস্টকে ভালোবাসার কথা বলছেন তখন ভেরলেন । র্যাঁবো ঠাট্টা করে তাঁকে লিখলেন যে ‘লয়োলা’ স্টুটগার্টে এলে দেখা হবে । লয়োলা ছিলেন এক যিশুভক্ত পাদ্রি ।
পরস্পরের সাক্ষাতের সেই মুহূর্তটা এলো এবং কমেডি ছাপিয়ে গেল ট্যাজেডিকে । ভেরলেন গোঁ ধরলেন র্যাঁবোকে দীক্ষিত করার জন্য, একটা শুঁড়িখানায় দুজনে একত্রিত হয়ে । ভেরলেন আর র্যাঁবো দুজনেই মাত্রাহীন মদ টেনে মাতাল হলেন এবং আবার কথা কাটাকাটি আরম্ভ হল । শুঁড়িখানা থেকে বেরিয়ে দুই বিখ্যাত কবির মধ্যে হাতাহাতি মারামারি আরম্ভ হল। র্যাঁবোর সঙ্গে পেরে ওঠা অসম্ভব ছিল ভেরলেনের পক্ষে । মার খেয়ে মাতাল ভেরলেন, রক্তাক্ত, পড়ে রইলেন পথের ধারে ।
সাত এম-এম ছয়গুলির পিস্তলটা ক্রিস্টির নিলামে কেউ ষাট হাজার ডলারে সম্প্রতি কিনে নিয়েছেন ; তার আগে পিস্তলটা ছয়বার নিলাম হয়েছিল । মায়ের দেয়া টাকায় ‘নরকে এক ঋতু’ ছাপিয়ে, মাকে এক কপি দিয়ে, কবিতার প্রতি র্যাঁবোর আকর্ষণ শেষ হয়ে গিয়েছিল ; ইল্যুমিনেশান্স’ আর ছাপাবার প্রয়োজন বোধ করেননি, যা করার কোরো বলে পাণ্ডুলিপি ভেরলেনকে দিয়ে পাড়ি দিয়েছিলেন আফ্রিকায়, ভিন্ন জীবনের সন্ধানে । ভেরলেন কবিতাগুলো মে-জুন ১৮৮৬-এ ‘প্যারিস লিটেরারি রিভিউতে’ প্রথমে প্রকাশ করার জন্য দেন । তারপর গ্রন্হাকারে প্রকাশের ব্যবস্হা করেন ১৮৮৬ সালের অক্টোবরে ।
 মলয় রায়চৌধুরী | 122.179.172.247 | ৩০ আগস্ট ২০২১ ১২:৪৩734911
মলয় রায়চৌধুরী | 122.179.172.247 | ৩০ আগস্ট ২০২১ ১২:৪৩734911শার্ল বোদলেয়ার আর ফিওদর দস্তয়েভস্কি
মলয় রায়চৌধুরী
দুশো বছর আগে জন্মেছিলেন এনারা দুজন, ১৮২১ সালে : কবি শার্ল বোদলেয়ার, এপ্রিল মাসে আর কথাসাহিত্যিক ফিওদর দস্তয়েভস্কি নভেম্বর মাসে, আর দুজনেই, দর্শন, বুনন, দৃষ্টিপ্রতিভা ও শৈলী-জগতে এনেছিলেন বিস্ময়কর বাঁকবদল, সূত্রপাত ঘটিয়েছিলেন পুঁজিবাদের গর্ভে জন্ম নেয়া ও আব্রাহামিক যূগ্মবৈপরীত্যের বা বাইনারি-অপোজিটের জাঁতাকলে রক্তাক্ত আধুনিকতাবাদী মননবিশ্বের। বোদলেয়ার মারা যান ছেচল্লিশ বছর বয়সে এবং যে বইটির কারণে তিনি, জাঁ আর্তুর র্যাঁবো’র কথায় “প্রথম দ্রষ্টা তিনি, কবিদের রাজা, এক সত্য দেবতা”, সেই বইটি রবীণ্দ্রনাথের জন্মের ছয় বছর আগে ১৮৫৭ সালে প্রকাশিত হয়েছিল,আর সেই সময়ে ভারতীয় সিপাহিরা আরম্ভ করেছিল মহাবিদ্রোহ।
বোদলেয়ারের বইটির নাম রেখেছিলেন ‘লা ফ্ল্যুর দ্য মাল’ (Les Fleurs du mal ), যার বাংলা কলাকৈবল্যবাদী অধ্যাপক বুদ্ধদেব বসু করেছেন ‘ক্লেদজ কুসুম’, যদিও ক্যাথলিক খ্রিস্টধর্ম অনুযায়ী নামটি হওয়া উচিত ‘শয়তানের ফুল’। ‘ইভিল’ শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ বুদ্ধদেব বসু করেছিলেন ‘ক্লেদ’, সুরভি বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ‘শার্ল বোদলেয়ার : অনন্য দ্রষ্টা’ বইতে করেছেন ‘পাপ’ । বাঙালি কবিরা বোদলেয়ারের জীবন ও কবিতার সঙ্গে পরিচিত হন জীবনানন্দ দাশ-এর মৃত্যুর বছর, ১৯৫৪ সালে, বুদ্ধদেব বসুর মাধ্যমে। যে বোদলেয়ার বলেন ‘পাপকর্মের চৈতন্যই মহত্তর রতিসুখসার’, যে বোদলয়ার ‘দস্তয়েভস্কির প্রিন্স মিশকিনের মতো’, যিনি মনে করতেন ‘রূপসী’ ও ‘বিষাদময়ী’ প্রায় সমার্থক, যিনি বলতেন ‘মানুষ দুঃখী, কিন্তু সে জানুক সে দুঃখী, মানুষ পাপী, কিন্তু সে জানুক সে পাপী; মানুষ রুগ্ন, কিন্তু সে জানুক সে রুগ্ন’, সেই নিদারুণ আত্মোপলদ্ধির সঙ্গে বুদ্ধদেব বসু পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন উঠতি বাঙালি কবিদের, । তবে বুদ্ধদেব বসু আদালতের দ্বারা নিষিদ্ধ আর ‘শয়তানপন্হী’ কবিতাগুলো অনুবাদ করেননি বিশেষ করে ‘কেন ও অ্যাবেল’ কবিতাটা । এই কবিতাটি, বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন ওয়ালটার বেনিয়ামিন, শার্ল বোদলেয়ার শাসকের অন্যায় ও সাম্রাজ্যবাদকে কতটা সমার্থক মনে করতেন। তাঁর কালখণ্ডের পূঁজিবাদীঁ-গরলনদীর তীরে ভিখারি, ভবঘুরে, গৃহহীন, দুর্দশা-আক্রান্ত, দুঃখি, যাদের উচ্ছেদ করা হয়েছে তারাই সর্বহারা। এই সর্বহারাদের ‘শ্রেণী’ না নলে বোদলেয়ার বলেছেন ‘জাতি’। বোদলেয়ার আর দস্তয়েভস্কি আলোচনার সময়ে যে-দুজন বাঙালির কথা মনে পড়ছে তাঁরা হলেন ঋত্বিক ঘটক আর ক্ষেত্র গুপ্ত।
দস্তয়েভস্কির তুলনায় বোদলেয়ারের বইয়ের সংখ্যা অনেক কম ; ১৮৪৭ সালে ‘লা ফানফার্লো’ ১৮৫৭ সালে ‘ক্লেদজ কুসুম’, ১৮৬০ সালে ‘নকল স্বর্গ’, ১৮৯৭ সালে ‘অন্তরঙ্গ জার্নাল’; তাছাড়া কয়েকটি প্রবন্ধ। দস্তয়েভস্কি লিখেছিলেন চোদ্দটি উপন্যাস ও আটটি গল্পের বই । বোদলেয়ার তাঁর কবিতাগুলো প্রকাশের আগে প্রুফ দেখার পর্যায়েও পরিবর্তন করতেন । তাঁর প্রকাশক পোলে মালাসি মৃত্যুর আগে লিখে গিয়েছেন যে তাঁর আলমারিতে ‘ফ্ল্যর দু মাল’ বইটির একটা প্রুফ-কপি রাখে আছে, যা দেখে জানা যাবে একজন কবির নিখুঁত হবার আপোসহীন প্রয়াস, আর তার প্রকাশকের অলৌকিক সহিষ্ণুতা । দস্তয়েভস্কির বইয়ের প্রুফ দেখে দিতেন তাঁর স্ত্রী আনা ।
সমাজের ভাঙনে যে ‘নতুন অন্যায়’ জেগে উঠছিল মানুষের আর্থ-রাজনৈতিক জীবনে, সেই সময়ে তা নিয়ে চিন্তিত ছিলেন কার্ল মার্কস নামে এক জার্মান যুবক, যিনি পরিবর্তনের নকশার কথা ভেবে প্রকাশ করলেন ‘দাস ক্যাপিটাল’ ( ১৮৬৭ - ১৮৮৩ ) গ্রন্হ এবং সহভাবুক ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস-এর সঙ্গে কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো ( ১৮৪৮ ) । বোদলেয়ার এবং দস্তয়েভস্কি, অতএব, কার্ল মার্কসের মতনই পরিবর্তনরত সমাজ ও তার মানুষদের আঁচ করতে পেরেছিলেন । উনিশ শতকের ইউরোপে শহরগুলো দ্রুত, অভূতপূর্ব বিশাল আকারে এমন ভাবে বেড়ে উঠছিল যে শহরবাসীর অভিজ্ঞতায় সুদূরপ্রসারী চাপ সৃষ্টি করছিল তারা । বোদলেয়ারের ভাবকল্প ‘ফ্ল্যনিয়র’ বা পথচর, জন্মেছিল এই নকশাটি থেকে , আধুনিকতাবাদের প্রথম চারিত্র্যবৈশিষ্ট্যের অন্যতম । গ্রামাঞ্চল থেকে এসে বিশাল মহানগরের ভুলভুলাইয়ায় নিজেকে হারিয়ে ফেলছিল ব্যক্তি-একক । গ্রামাঞ্চলে সে ছিল কৌমের অংশ , সবুজ ভূখণ্ডের অংশ । মহানগরের জটিল ও সর্পিল পথসমষ্টির বিভ্রান্তিকর বস্তি,রাস্তা, পথ, গলি, তস্যগলির ভুলভুলাইয়ায় তার কৌমপ্রতিস্ব ক্রমশ আবছা হয়ে জন্মাচ্ছিল ব্যক্তিএককের আধুনিক প্রতিস্ব । অবশ্য বোদলেয়ার এবং দস্তয়েভস্কি দুজনেরই মনে হয়েছিল যে দুর্ভোগ বহিরাগত কিছু নয়, এটি ব্যক্তি-মানুষের জীবনে অন্তর্নিহিত; যে কেউ কলঙ্কিত সমাজ থেকে শারীরিকভাবে পালাতে পারে, কিন্তু মনের কলঙ্ক থেকে নয়; যেভাবেই সমাজকে পুনর্গঠন করা হোক না কেন, দুর্ভোগের শেষ হয় না।
বোদলেয়ারের প্যারিস এবং দস্তয়েভস্কির পিটার্সবার্গের ভুলভুলাইয়াগুলোতে গড়ে উঠছিল গোপন ও নিষিদ্ধ পরিসর, যা ছিল একযোগে ভয়ের এবং আনন্দলাভের এলাকা ; সেই পরিসরে বক্তিমানুষ , বিশেষ করে পুরুষ, এলাকাটির অংশ হয়েও আক্রান্ত হচ্ছিল পারস্পরিক দূরত্বে, অসম্বদ্ধতায়, অপসৃতির বোধে । আধুনিকতা ইউরোপের দেশে-দেশে গড়ে তুলছিল মহানগর, এবং সেই মহানগরগুলোয়, আধুনিকতার অবদানরূপে দেখা দিচ্ছিল আলোকময়তার পরিসর ও অন্ধকারাচ্ছন্নতার পরিসর ; বৈভবশালীর এলাকা ও ভিখারি জুয়াড়ি নেশাখোর যৌনকর্মী অপরাধী ও শ্রমিকদের এলাকা । যুগ্মবৈপরীত্যের বিভাজন । দান্তে কখনও তাঁর নরকের পাপীদের জন্য কোনও অন্তর্মুখী যন্ত্রণা অনুভব করেননি, যে-যন্ত্রণা নিজেদের জীবনে পেয়েছিলেন বোদলেয়ার ও দস্তয়েভস্কি এবং তা নিজেদের রচনায় উপস্হাপন করে গেছেন । বোদলেয়ারের মতনই দস্তয়েভস্কি কথা বলতে পছন্দ করতেন, কিন্তু তোতলা দস্তয়েভস্কি ভালো বক্তা ছিলেন না। মৃগীরোগ ছিল বলে অনেক তাঁকে মাথাখারাপ লোক মনে করতো । পক্ষান্তরে বোদলেয়ার ছিলেন বাগ্মী এবং শ্রোতাদের তাঁর নতুন-নতুন বক্তব্য শুনিয়ে অবাক করে দিতেন, যদিও শেষ বয়সে পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে তিনি মূক হয়ে গিয়েছিলেন ।
দস্তয়েভস্কি মারা যান ষাট বছর বয়সে । ১৮৬২ সালে তিনি ফ্রান্সে গিয়েছিলেন, কিন্তু বোদলেয়ারের খ্যাতি বা কুখ্যাতির কথা জানতেন না এবং ইউরিপীয়দের, বিশেষ করে ফ্রান্সের লোকেদের আর সেখানকার শিল্পকর্ম তাঁর পছন্দ হয়নি । যদিও ‘বিষণ্ণ প্যারিস’-এর নিচুতলার মানুষেরা যেমন বোদলেয়ারকে, তেমনই দস্তয়েভস্কির শিল্পীমানসকে বরাবরই প্রভাবিত করেছে সেই ধরনের মানুষজন যারা আটপৌরে নয় । দুজনকেই আকৃষ্ট করেছে ব্রাত্য, অপমানিত, নিপীড়িত, ভেঙেপড়া মানুষ । তাঁদের চরিত্রে তফাত হলো যে দস্তয়েভস্কি মদ প্রায় খেতেন না ; তিনি মনে করতেন, মদ মানুষকে পশু বানিয়ে ফেলে, তার কোমলতাকে নষ্ট করে দেয় । বোদলেয়ার বেশ্যালয়ে যেতেন, মদ-চরস-আফিম খেতেন এবং তাঁর অভিজ্ঞতার কথা লিখে গেছেন ‘নকল স্বর্গ’ রচনায় । মৃত্যু, যন্ত্রণা, ক্লেদ, দুঃখ, বিষাদ, বিতৃষ্ণা, বিবমিষা, পাপ ও পতন এসবই বোদলেয়ারের বিপুল আগ্রহের বিষয় ছিল। বোদলেয়ার ছিলেন নিশাচর এবং পথে-পথে ঘুরে মানুষের অন্তরবেদনার সঙ্গে পরিচিত হতেন, তেমনই লেখালিখির এক ফাঁকে দস্তয়েভস্কি খবরের কাগজের দোকানে গিয়ে পাতা উল্টে বিচিত্র ঘটনা আর মানুষের খোঁজ করতেন যাতে তিনি সেগুলো তাঁর উপন্যাসের উপাদান হিসাবে ব্যবহার করতে পারেন, আর অনেক সময়ে অবাক হতেন যে তিনি উপন্যাসের জন্য ঘটনাগুলো আগেই ভেবেছিলেন । দস্তয়েভস্কির ছিল জুয়ার নেশা আর তাতেই তিনি বহুবার ফেঁসেছেন।
দুজনেরই শৈশবের অভিজ্ঞতা বয়ে বেড়িয়েছেন সারাজীবন। তাঁরা বিচ্ছিন্ন পরিবারের মধ্যে নিজেদের মানিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। শৈশবে মাতৃহারা দস্তয়েভস্কি বাবার কঠিন শাসনের মধ্যে যেমন আত্মীয় বলে কাউকে পাননি, তেমনই পরিবারের বাইরে কাউকে বন্ধু বলেও মেনে নিতে পারেননি। বাবাকে তিনি শ্রদ্ধা করতে পারেননি । বোদলেয়ারের বাবা মারা যাবার পর তাঁর মা আবার বিয়ে করেন, যাঁকে বোদলেয়ার বাবার আসনে বসাতে পারেননি । দুজনেরই যৌবন কেটেছে ব্যর্থ মানুষদের কাছাকাছি ; বোদলেয়ার তা বেছে নিয়েছিলেন নিজেই আর দস্তয়েভস্কি বাধ্য হয়েছিলেন। অমন জীবনযাত্রা তাঁদের গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। বোদলেয়ার মাদক ও যৌনতার কারণে উপদংশে আক্রান্ত হন যা শেষ পর্যন্ত তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়েছিল । এনারা দুজনেই মানুষের অন্তঃকরণের অসামাজিক রূপের ছবি গড়ে তুলেছেন । দস্তয়েভস্কি পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে তা ফুটিয়ে তুলতে প্রয়াসী হয়েছেন যখন কিনা বোদলেয়ার বলেছেন ‘অদৃশ্যকে দেখতে হবে, অশ্রুতকে শুনতে হবে, ইন্দ্রিয়সমূহের বিপুল ও সচেতন বিপর্যয় সাধনের দ্বারা পৌঁছাতে হবে অজানায়, জানতে হবে প্রেমের, দুঃখের, উন্মাদনার সব প্রকরণ; খুঁজতে হবে নিজেকে, সব গরল আত্মসাৎ করে নিতে হবে, পেতে হবে অকথ্য যন্ত্রণা, অলৌকিক শক্তি, হতে হবে মহারোগী, মহাদুর্জন, পরম নারকীয়, জ্ঞানীর শিরোমণি। আর এমন করেই অজানায় পৌঁছোনো যাবে ।’ তবে তা করতে গিয়ে নিজেদের তীব্র অন্তর্দাহকে এনারা এড়াতে পারেননি। এই কারণেই তাঁদের কবিতায় ও কথাসাহিত্যে মানুষেরা যন্ত্রণার শরিক, এক তীব্র কালখণ্ডের অংশীদার। তারা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেদের চারদিকেই এক সংকীর্ণ পরিমণ্ডল রচনা করে। দু’জনই নির্মোহ সাহিত্যিক, মহৎ সাহিত্যিক । বোদলেয়ার বিয়ে করেননি ; কৃষ্ণাঙ্গী প্রেমিকা জাঁ দুভাল ছিলেন তাঁর রক্ষিতা এবং মেয়েটির আচরণ অপছন্দ করা সত্বেও তাকে ছাড়েননি ; তা ছাড়া আরও দুজন নারীকে ভালোবেসেছিলেন, মাদাম সাবাতিয়ে ও মারি দ্যবরু, যাঁদের উপস্হিতি পাওয়া যায় তাঁর কবিতায় । বোদলেয়ার বলেছিলেন, ‘আধুনিকতা বলতে আমি বুঝি যা ক্ষণস্থায়ী, দ্রুত অপসৃয়মান, অনিয়ত ; এ হলো শিল্পের অর্ধেক এবং বাকি অর্ধেক হলো শাশ্বত এবং অপরিবর্তনীয়।’ এ যেন কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর সারকথা ।
বোদলেয়ার অংশগ্রহণ করেছিলেন ১৮৪৮ সালের ফরাসি বিপ্লবে, জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়েছিলেন ছাত্রদের সভায়, এবং বুইসঁর স্মৃতিচারণ অনুযায়ী, চব্বিশে ফেব্রুয়ারি বোদলেয়ারকে দেখা গিয়েছিল হাতে রাইফেল, গুলি চালাচ্ছেন বলে চোখেমুখে উত্তেজনা । সাতাশে ফেব্রুবারি তাঁকে দেখা গিয়েছিল ‘সালাই পুবলিক’ ( গণ সেলাম ) পত্রিকা ফিরি করছেন । ধড়পাকড় আরম্ভ হলে বোদলেয়ার দিজঁ চলে যান । লুই নেপোলিয়ান ক্ষমতা দখল করে নিজেকে সম্রাট ঘোষণা করলে বোদলেয়ারসহ কবি-শিল্পীদের স্বপ্নভঙ্গ হয় । রাজনীতি-করা ত্যাগ করেন তিনি। সমসময়ে, ১৮৪৯-এর এপ্রিলে, বিপ্লবী আর রাষ্ট্রবিরোধী হওয়ার দায়ে জার প্রথম নিকোলাস বন্দী করেছিলেন দস্তয়েভস্কিকে । পাঁচ বছর সাইবেরিয়ায় কারাগারে বন্দী থাকার পর ১৮৫৪ সালে মুক্তি পান তিনি । অবশ্য পুরোপুরি মুক্তি ঠিক বলা চলে না, পরের পাঁচ বছরের জন্য সাইবেরিয়ান রেজিমেন্টের সপ্তম ব্যাটেলিয়নে লেফটেনেন্ট হিসেবে কাজ করতে হয় লেখককে। এরই মধ্যে ১৮৫৭ সালে তিনি প্রেমে পড়েন মারিয়া দিমিত্রিয়েভনা ইসায়েভার, যিনি ছিলেন এক মাতালের স্ত্রী, যাঁকে তিনি বিয়ে করেন তাঁর স্বামী মারা যাবার পর, কিন্তু বিয়ের রাতেই তিনি মৃগী-আক্রান্ত হয়ে মুখে গ্যাঁজলা উঠে এমন ছটফট করতে থাকেন যে মারিয়া ভয় পেয়ে যান ; মারিয়ার সঙ্গে তিনি সুখি হতে পারেননি । দস্তয়েভস্কির মায়ের নামও ছিল মারিয়া, যিনি যক্ষ্মায় মারা যান, তখন দস্তয়েভস্কির বয়স পনেরো ; দস্তয়েভস্কির বাবাকে তাঁর ভূমিদাসরা খুন করে তাঁকে অনাথ করে দিয়েছিল ।
তার আগে দস্তয়েভস্কি প্রথম প্রেমে পড়েছিলেন আভদোতয়া ইয়াকোভলেভনার, ১৮৪০ সালে, যাঁকে তিনি বলতেন কুহকিনী, কিন্তু যুবতীটি তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেন । ১৮৬২-১৮৬৩ সালে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন চাষীর সুন্দরী মেয়ে আপোলিনা সুসলোভার সঙ্গে ; আপোলিনা তাঁকে যাতনা ছাড়া আর কিছুই দেয়নি । মেয়েটির আরেক স্পেনীয় প্রেমিক ছিল আর দস্তয়েভস্কির জুয়া খেলার নেশার দরুন তাঁদের সম্পর্ক বেশিদিন টেকেনি । ১৮৫৮ সালে ডিভোর্সি অভিনেত্রী আলেকজান্দ্রা ইভানোভা শুবার্তের সঙ্গে সম্পর্ক পাতান দস্তয়েভস্কি, যা বেশিদিন বজায় রাখতে পারেননি । এরপর ১৮৬৪-১৮৬৫ সালে তিনি এলিজাভেতা আন্দ্রেয়েভনা শ্লেবনিকোভার প্রেমে পড়েন ; সেই সম্পর্ক ভেঙে যায় কেননা দস্তয়েভস্কি জানতে পারেন যে যুবতীটি আরও অনেকের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক পাতিয়েছে । ১৮৬৫ সালে দস্তয়েভস্কির সঙ্গে পরিচয় হয় আনা কোরভিন-ক্রুকোভস্কায়ার, কিন্তু এই যুবতীও তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে। দস্তয়েভস্কির বন্ধু মিলিউকভ তাঁকে একজন সচিব রাখার পরামর্শ দিলে তিনি পাভেল ওলখিনের ছাত্রী বিশ বছর বয়সী আনা গ্রিগরিয়েভনা স্নিটকিনাকে নিয়োগ করেন এবং যুবতীটির শর্টহ্যান্ড দস্তয়েভস্কিকে অল্প সময়ে ‘দি গ্যাম্বলার’ সম্পূর্ণ করতে সাহায্য করে । ১৮৬৭ সালে দস্তয়েভস্কি বিয়ে করেন তাঁর চেয়ে পঁচিশ বছর ছোটো আনাকে । যখন জুয়াড়ি দস্তয়েভস্কি বারবার কিছু জিনিসপত্র বন্ধক রেখে ক্যাসিনোতে টাকা খোয়াচ্ছিলেন, তখন আনার সাহচর্য না পেলে তাঁর বহু রচনা লেখা হতো না, এমনকী রচিত লেখাও হারিয়ে যেতো । আনাকে বিয়ে করে তিনি চার সন্তানের বাবা হয়েছিলেন ।
আনা দুটি জীবনী লিখে গেছেন দস্তয়েভস্কির ‘আনা দস্তোয়েভস্কায়ার ডায়েরি’, যা তাঁর মৃত্যুর পরে ১৯২৩ সালে প্রকাশিত হয়েছিল এবং ১৯২৫ সালে প্রকাশিত ‘আনা দস্তয়েভস্কায়ার স্মৃতি’ । আনা বর্ণনা করেছেন দস্তয়েভস্কি কীভাবে তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন একটি কাল্পনিক নতুন উপন্যাসের প্লটের রূপরেখা দিয়ে, যেন নারীর মনোভাবের বিষয়ে তাঁর পরামর্শ প্রয়োজন। গল্পে একজন বয়স্ক চিত্রশিল্পী একটি অল্প বয়সী মেয়েকে প্রস্তাব দেন যার নাম অন্যা। দস্তয়েভস্কি জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে এত অল্প বয়সী এবং ব্যক্তিত্বের দিক দিয়ে আলাদা কোনও মেয়ের পক্ষে ওই চিত্রশিল্পীর প্রেমে পড়া কি সম্ভব? আনা উত্তর দিয়েছিলেন যে তা নিশ্চয়ই সম্ভব। তারপর তিনি আনাকে বললেন: "নিজেকে এক মুহুর্তের জন্য তার জায়গায় রাখো। কল্পনা করো আমি ওই চিত্রকর, আমি তোমার কাছে স্বীকার করছি যে তোমাকি আমি আমার স্ত্রী হতে বলছি। তুমি কী উত্তর দেবে?" আনা বলেছিলেন: "আমি উত্তর দেব যে আমি তোমাকে ভালবাসি এবং আমি তোমাকে চিরকাল ভালবাসব"।
বোদলেয়ার আর দস্তয়েভস্কিকে আধুনিকতাবাদী সাহিত্যের জনক এই জন্য বলা হয় কেননা তাঁরা খ্রিস্টধর্মকে সন্দেহ করার সূচনা করেছিলেন, কবিতায় বোদলেয়ার ‘ক্লেদজ কুসুম’, ‘প্যারিস স্প্লিন’ এবং তাঁর “অন্তরঙ্গ জার্নাল’-এ, আর দস্তয়েভস্কি তাঁর উপন্যাসে, রাসকলনিকভ চরিত্র (ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিশমেন্ট ), করাজাজভ ভাই এবং প্রিন্স মিশকিন ('দ্য ইডিয়ট’) চরিত্র সৃষ্টির মাধ্যমে। এনাদের ভাবনার মিলগুলো বিস্ময়কর । দুজনেই আঠারো শতকের যুক্তিবাদ নিয়ে অসন্তুষ্ট আর ইউটিলিটেরিয়ানিজমকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন । বোদলেয়ারই যেন দস্তয়েভস্কির ‘নোটস ফ্রম দি আণ্ডারগ্রাউণ্ড’-এর অ্যান্টি-হিরো, যাঁর কবিতার ‘আমি’ দস্তয়েভস্কির চরিত্রটির মতো নামহীন । দস্তয়েভস্কির ‘নোটস ফ্রম দি আণ্ডারগ্রাউন্ড’ যেন এক বোদলেয়ারিয় জগত, যেখানে সংস্কারক একজন ‘বোকা’, অগ্রগতির অর্থ নৈতিক অবক্ষয় । বোদলেয়ারের কবিতার জগতের মতনই উভয় ক্ষেত্রেই নায়করা অসুস্থ, শারীরিকভাবে দুর্বল, তাদের ইচ্ছাশক্তির অভাব এবং যন্ত্রণায় ভোগে । বোদলেয়ারের কবিতার মতনই দস্তয়েভস্কির বনেদ গড়ে উঠেছে স্বগতোক্তি আর স্বীকারোক্তিতে । উনিশ শতকের প্যারিস মহানগরের পথে-পথে টহলক্রিয়াকে চিহ্ণিত করে শার্ল বদল্যার একটি ভাবকল্প তৈরি করে দিয়ে গেছেন । ক্রিয়াটিকে তিনি বলেছেন ‘ফ্ল্যানেরি’ এবং ওই পথচর দর্শককে বলেছেন ‘ফ্লনিয়র’। এনিড স্টার্কি বলেছেন যে ওয়র্ডসওয়র্থের একেবারে ভিন্ন মেরুর ভাবনা ছিল বোদলেয়ারের, কেননা বোদলেয়ার কবিতার খসড়া লিখেছেন তীব্র আবেগের মুহূর্তে ।
অ্যাঞ্জেলা কার্টার, নারীবাদী আলোচক, শার্ল বোদলেয়ারের সমালোচনা করেছেন জাঁ দুভাল-এর দৃষ্টিতে, তাঁর "ব্ল্যাক ভেনাস" বইতে । একজন ক্রেওল যুবতী, যাঁর মা-বাবা-দেশ সম্পর্কে বেশি কিছু জানা যায়নি, সেই মহিলাকে কবিতার লেখক, পাঠকের স্বার্থে, দ্বৈত অর্থে ‘অপর ভোগ্য নারী’ হিসেবে তুলে ধরেছেন । তার গায়ের রঙ কালো এবং উনিশ শতকে ইউরোপে মনে করা হতো ‘অন্ধকার’ ত্বকের নারীদের যৌনতা শ্বেতাঙ্গিনীদের তুলনায় তীব্র, তারা দূষিত এবং রোগাক্রান্ত বলে আকর্ষক । কার্টার বলেছেন, বহিরাগত নারীত্বের অন্যান্য দর্শকদের মতো, বোদলেয়ারও জাঁ দুভাল-এর চেহারা দেখে মুগ্ধ হন: তার চুল, তার ঘ্রাণ এবং তার কোমলতা তাঁকে যৌন উত্তেজনা দেয় । নারীটি বিশেষ ব্যক্তিত্বের অধিকারী নন। বোদলেয়ার তাঁকে পশুর মতো, প্রাকৃতিক ব্যক্তিত্ব হিসাবে বিবেচনা করেছেন। পথচর বোদলেয়ার এমন লোকদের সন্ধান করতেন যারা উপেক্ষিত ও সমাজে প্রত্যাখ্যাত । বোদলেয়ারের চোখে সমাজের এই প্রত্যাখ্যানগুলি ছিল সৃজনশীল শিল্পের উপাদান। বোদলেয়ারের ‘অ্যা উন দ্যাম ক্রেয়োলে’ ( A une Dame cre’ole ), জাঁ দুভালকে নিয়ে লেখা, ছিল তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতা ।
শার্ল বোদলেয়ারের ‘ফ্ল্যুর দু মাল.ৱ’ আর ফিওদর দস্তয়েভস্কির ‘দ্য গ্যাম্বলার’ দুটিই অসাধারণ দৃষ্টিপ্রতিভা সম্বলিত কাজ । দুজনেই জুয়া, প্রেম, ভাগ্য, নৈতিক অবক্ষয় এবং গভীর দারিদ্র্যের বিষয় নিয়ে কাজ করেছেন। বোদলেয়ার লিখেছিলেন প্রতীকবাদের যুগে, যে আন্দোলন ১৮৬০ থেকে ১৮৮০-এর মাঝে ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রতীকবাদের মূল বিষয় ছিল অন্ধকার আর ক্ষয়কে ঘিরে । পক্ষান্তরে দস্তয়েভস্কি রাশিয়ায় অস্তিত্ববাদী এবং প্রতীকবাদী আন্দোলনের সময়ে উপন্যাসগুলো লিখছিলেন । তাঁর কবিতার দরুন বোদলেয়ারকে বলা হতো শয়তানপন্হী কবি, কেননা তিনি খ্রিস্টধর্মের যূগ্মবৈপরীত্যের ‘অপর’কে সমর্থন করতেন । দস্তয়েভস্কির মতনই তাঁর উপন্যাসের চরিত্রগুলোর মধ্যে অন্তত এক-চতুর্থাংশ নানা রকম মানসিক জটিলতা বা ব্যাধিতে ভোগে। বারোটি উপন্যাসের মধ্যে পাঁচটিতে এ রকম চরিত্র দেখতে পাওয়া যায়। তাদের কারো কারো খিঁচুনি হয়, যাদের অন্তত পাঁচজন মৃগীরোগের শিকার, অন্যদের হিস্টিরিয়াসহ অন্যান্য জটিলতা আছে । চরিত্রের খিঁচুনি ও অন্য উপসর্গগুলো দস্তয়েভস্কি তাঁর উপন্যাসে উনিশ শতকের চিকিৎসাবিজ্ঞানে ও সমাজে প্রচলিত শব্দের সাহায্যে বর্ণনা করেছেন।
বোদলেয়ারের বিপরীত দস্তয়েভস্কি ছিলেন ঈর্ষাকাতর মানুষ। নিজের স্ত্রীর দিনানুদৈনিককে তিনি নিয়ন্ত্রণ করতেন। ঠোঁটে লিপস্টিক দেওয়া, অন্য পুরুষের সামনে হাসার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন, যখন কিনা বোদলেয়ার লিখেছেন যে সাজগোজ করা নারীর জন্য জরুরি কেননা তা প্রকৃতির দেয়া সাধারণ রূপে সৌন্দর্য আরোপ করে ; শিল্পীদের তেমনই উচিত প্রকৃতির আরোপ করা রঙ ও আকারকে বদলে ফেলা । এই প্রসঙ্গে লেভ তলস্তয়ের বক্তব্য উল্লেখ্য : “ আমি বর্তমান কালে মহৎ কবি বলে স্বীকৃত বোদলেয়ার এবং ভেরলেন নামক দুজন কবির আশ্চর্য খ্যাতির বিষয়ে কিছু বলতে চাই। যে ফরাসি লেখদের মধ্যে ছিলেন শ্যেনিয়ে, মুসে, লা মার্তিন, এবং সর্বপরি উগো এবং যাদের মধ্যে সাম্প্রতিককালে লেকঁৎ দ্য লীল, স্যুলি প্রুধোম প্রমুখ তথাকথিত পার্নাসিয়ানেরা আবির্ভূত হয়েছিলেন, তাদের অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও রূপকর্মের দিক থেকে কলাকুশলতাহীন এবং বিষয়বস্তু উপস্থাপনার দিক থেকে অত্যন্ত ধিক্কারযোগ্য এমন দুজন পদ্য লেখককে ফরাসিরা কী করে এত মূল্য দিলেন তা আমার বুদ্ধিরও অগম্য। তাদের মধ্যে বোদলেয়ারের জীবনদর্শন ছিল স্থূল অহংবাদকে একটা তত্ত্বের স্তরে উন্নীত করা এবং নৈতিকতার স্থলে ধোঁয়াটে সৌন্দর্য-কল্পনা, বিশেষভাবে কৃত্রিম সৌন্দর্য স্থাপন করা। বোদলেয়ারের নিকট নারীমুখের স্বাভাবিক সৌন্দর্য থেকে তার প্রসাধিত মুখের সৌন্দর্যের প্রতি এবং প্রকৃত বৃক্ষ এবং স্বাভাবিক জল থেকে ধাতব বৃক্ষ এবং রঙ্গমঞ্চে অনুকৃত জলের প্রতি ছিল অধিকতর পক্ষপাত এবং তা তিনি প্রকাশও করেছেন।” দস্তয়েভস্কি ও তলস্তয় এবং একই সাহিত্য সমাবেশে দুজনে উপস্হিত থেকেও পরস্পরের সঙ্গে দেখা করেননি । তলস্তয় মনে করতেন দস্তয়েভস্কির রচনায় আছে অতিরঞ্জন, অসম্ভবতা ; তাছাড়া দস্তয়েভস্কির "আকারহীন শৈলী", ব্যাকরণগত ত্রুটি, চরিত্রদের মৃগীরোগ, মদ্যপান, উন্মাদরা উপন্যাসের মঞ্চে ভিড় করে বলে মনে করতেন। উল্লেখ্য যে দস্তয়েভস্কির মতন তলস্তয়ও জুয়াড়ি ছিলেন ।
সম্ভবত শেক্সপিয়র এবং ফ্রানৎস কাফকা ছাড়া আর কেউ দস্তয়েভস্কির মতন ট্র্যাজিক চরিত্র গড়ে তুলতে পারেননি । ‘ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট’-এর খুনি রাসকলনিকভ, যে আত্মার শুদ্ধিকরণের জন্য যৌনকর্মীর পায়ের কাছে নত হয় এবং বলে ওঠে, “তোমার সামনে আমি সাষ্টাঙ্গ হচ্ছি, যাতে তোমার মাধ্যমে যন্ত্রণাকাতর মানবের সামনে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানাতে পারি ।” দস্তয়েভস্কির মতন বোদলেয়ারও মনে করতেন কবি-সাহিত্যিককে মানুষের অন্তরলোকের উন্মোচন করতে হবে । সুতরাং বুদ্ধদেব বসুর কলাকৈবল্যবাদ প্রয়োগ করে এনাদের গভীরে প্রবেশ করা সহজ নয় । ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের দার্শনিক ওয়াল্টার বেনিয়ামিন ‘শার্ল বোদলেয়ার : এ লিরিক পোয়েট ইন দি এরা অফ হাই ক্যাপিটালিজম’ রচনায় বলেছেন, কলাকৈবল্যবাদী দৃষ্টিতে বোদলেয়ারকে বস্তুজগৎবিচ্ছিন্ন শব্দ আর চিত্রকল্পের কবি মনে করা ভুল ; প্রকৃতপক্ষে বোদলেয়ার হলেন নতুন গজানো পুঁজিবাদের একজন গুরুত্বপূর্ণ লিরিক কবি, মেট্রোপলিসের কবি, যিনি আধুনিকতা যে ‘শক-ওয়েভ' তৈরি করেছিল, তার কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছিলেন । অর্থাৎ বোদলেয়ারের কবিতা বাজার-সংস্কৃতির একটি বিশেষ পর্যায়কে তুলে ধরেছে এবং এ কারণেই ওই বাজার-সংস্কৃতির আলোচনা বাদ দিয়ে বোদলেয়ারকে বিশ্লেষণ করা যায় না ।
ফ্রেডরিক নীৎশে লিখেছেন, দস্তয়েভস্কির রচনার সঙ্গে পরিচিতি তাঁর জীবনের "সবচেয়ে সুখী আবিষ্কারগুলির অন্তর্গত"। তিনি দস্তয়েভস্কিকে একজন প্রতিভা হিসাবে বিবেচনা করেছিলেন, যিনি বিশ্বজগতের সাথে ব্যঞ্জনাযুক্ত, "একমাত্র মনোবিজ্ঞানী" যাঁর কাছ থেকে তিনি জীবনশিক্ষা পেয়েছেন। ফ্রান্ৎস কাফকা, মহিলাবন্ধু ফেলিসিয়া বাউরকে লিখেছিলেন, দস্তয়েভস্কির সঙ্গে তিনি "রক্তের সম্পর্ক" বোধ করেন। সিগমুণ্ড ফ্রয়েড দস্তয়েভস্কিকে শেক্সপিয়ারের সাথে একাসনে বসিয়েছিলেন এবং "দ্য ব্রাদার্স কারামাজভ" বইটিকে কালের সবচেয়ে উন্নত উপন্যাস বলে অভিহিত করেছিলেন। কুরোসাওয়া স্বীকার করেছিলেন যে তিনি ছোটবেলা থেকেই দস্তয়েভস্কিকে ভালোবাসতেন কারণ তিনি জীবন সম্পর্কে খোলাখুলি লিখে গেছেন । কুরোসাওয়া একথাও বলেছিলেন যে দস্তয়েভস্কি "মানুষের সীমানা" অতিক্রম করে ঐশী বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে পেরেছেন । অ্যালবার্ট আইনস্টাইন বলেছিলেন যে দস্তয়েভস্কির রচনাগুলো তাঁকে চূড়ান্ত সুখের অনুভূতি দেয়। এই অনুভূতিটি ধরার জন্য, কাজের মাহাত্ম্য বুঝতে, তাঁকে শিল্প-সাহিত্য সমালোচক হওয়ার দরকার নেই। তিনি স্বীকার করেছিলেন যে বিজ্ঞানের গবেষণা কখনই ‘দ্য ব্রাদার্স কারামাজভ’-এর মতো সৃষ্টির মূলে প্রবেশ করতে পারবে না। পরাবাস্তববাদ, অস্তিবাদ প্রভৃতি আধুনিক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রবক্তারা দস্তয়েভস্কির প্রভাবের কথা স্বীকার করেছেন। অনেক সমালোচক তো মনে করেন দস্তয়েভস্কির হাত ধরেই অস্তিবাদের উদ্ভব হয়েছিল। আর্নেস্ট হেমিংওয়ে, জেমস জয়েস, ভার্জিনিয়া উলফ, সিগমুন্ড ফ্রয়েড, আয়ান রান্ড, হেরম্যান হেস, হুলিও কোর্তাজার সকলেই তাঁকে পূর্বসূরী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন । জেমস জয়েস বলেছেন যে দস্তয়েভস্কি হলেন আধুনিক গদ্যবিন্যাসের নির্মাতা । আলবেয়ার কাম্যু বলেছেন যে দস্তয়েভস্কি হলেন একজন প্রফেট । আর লণ্ডনে রাইমার্স ক্লাবের প্রতিষ্ঠার সময় ইয়েটস বলেছিলেন যে, যা কিছু কবিতা নয়, তা থেকে মুক্তি দিতে হবে কবিতাকে এবং লিখে যেতে হবে বোদলেয়ার ও ভের্লেনের মতো করে। যা কিছু কবিতা নয়, তা থেকে কবিতার মুক্তির প্রথম দলিল, ‘ফ্ল্যর দ্যু মাল।’
মিখাইল বাখতিন তাঁর ‘প্রবলেমস অব দস্তয়েভস্কিজ পোয়েটিকস’ প্রবন্ধে পাঠকদের সামনে দস্তয়েভস্কির উপন্যাসের সমালোচনা করেছেন ডায়ালগিজম, হেটেরোগ্লসিয়া, ক্রনোটোপ, পলিফনি, কার্নিভাল সংক্রান্ত উত্তরাধুনিক তত্ত্বের মধ্য দিয়ে । ডায়ালগিজম কেবলমাত্র একমুখী ক্রিয়া বা সংলাপ নয়, তা জগৎ সম্বন্ধে জানার ও জীবন সম্পর্কে পরিচিত হবার এক ধারাবাহিক প্রক্রিয়া । দস্তয়েভস্কি একটি সম্পূর্ণ নতুন ধরণের শৈল্পিক চিন্তাভাবনা তৈরি করেছিলেন, যাকে বাখতিন বলেছেন পলিফোনিক। এই ধরণের শৈল্পিক চিন্তাভাবনা দস্তয়েভস্কির উপন্যাসগুলিতে স্হান পেয়েছে, তবে এর তাৎপর্য উপন্যাসের সীমা ছাড়িয়েও অনেক প্রসারিত এবং ইউরোপীয় নন্দনতত্ত্বের বেশ কয়েকটি মৌলিক ভাবনার সূত্রপাত ঘটিয়েছে । বাখতিন মনে করেন, দস্তয়েভস্কি বিশ্বের সাহিত্য-শিল্পের নতুন বনেদ গড়ে দিয়ে গেছেন । বাখতিন যুক্তি দিয়েছেন যে দস্তয়েভস্কির রচনাগুলি মূলত ‘সংলাপ’, স্বায়ত্তশাসিত কণ্ঠস্বর, কথোপকথনের বিপরীতে উদ্ঘাটিত মিথস্ক্রিয়া, যেখানে একক লেখক মহাবিশ্বের সীমানার মধ্যে প্লট এবং চরিত্রের উদ্ভব ঘটান । বাখতিনের মতে, দস্তয়েভস্কি পলিফোনিক উপন্যাসের স্রষ্টা ছিলেন এবং এটি একটি মৌলিকভাবে নতুন জেনার ছিল, যা পূর্বধারণাযুক্ত ফ্রেমওয়ার্ক এবং স্কিমা অনুযায়ী বিশ্লেষণ করা যায় না । বাখতিন মনে করেন যে দস্তয়েভস্কির উপন্যাসে চরিত্রদের তাদের বাইরের বিশ্বের আদেশে সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ না হওয়ার ক্ষমতা তাদের চেতনার অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। যদিও বাহ্যিক আপত্তি (সংজ্ঞা, বিবরণ, কার্যকারণ বা জিনগত ব্যাখ্যা ইত্যাদি) অনিবার্য, এটি কখনই পুরো সত্য নয় । এটিকেই বাখতিন একটি "একাত্ত্বিক" সত্য বলে অভিহিত করেছেন । বাখতিনের মতে, দস্তয়েভস্কি সর্বদা চিন্তার স্রোতের বিরোধিতা করে গেছেন (বৈজ্ঞানিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক ইত্যাদি) যাতে ব্যক্তি-একক বস্তুতে পরিণত না হয় । ফরাসি রেনেসাঁ যুগের লেখক ফ্রঁসোয়া রাবলের সমকক্ষ দস্তয়েভস্কিও প্রয়োগ করেছেন কার্নিভালেস্ক ঘটনাপ্রবাহ।উত্তর -আধুনিক দার্শনিকরা শার্ল বোদলেয়ারকে একজন ভবিষ্যবক্তার আসনে বসিয়েছেন, তাঁর ‘বিষণ্ণ প্যারিস’ বইয়ের শেষ কবিতাটির জন্য, ‘গরিবদের উপর আঘাত কর’! এটা অনেকটা আজকের রাজনীতিবিদদের ষড়যন্ত্রের মতন শোনায় ।
.
 মলয় রায়চৌধুরী | 122.179.172.247 | ৩০ আগস্ট ২০২১ ১২:৪৪734912
মলয় রায়চৌধুরী | 122.179.172.247 | ৩০ আগস্ট ২০২১ ১২:৪৪734912ভণ্ডামি : মলয় রায়চৌধুরী
মরিচঝাঁপিকে কেন্দ্র করে একটা ডিটেকটিভ উপন্যাস লেখার তোড়জোড় করছিলুম, তখনই কাজল সেন বললেন
ভণ্ডামি নিয়ে লেখা দিতে । ডিটেকটিভ উপন্যাসে একদল যুবক-যুবতী, যাদের মা-বাবা-দাদাদের গণহত্যা করা
হয়েছিল মরিচঝাঁপিতে, তারা ষড়যন্ত্র করেছে যে হত্যাকারীদের খুঁজে, তারা এখন যেখানেই থাকুক না কেন,
তাদের খুন করবে ; যুবক-যুবতীদের হাতে একটা সরকারি ফাইল এসেছে যা অনেকে ভেবেছিলেন হারিয়ে গেছে ।
সেই ফাইল থেকে গণহত্যায় যারা অংশ নিয়েছিল আর যারা গণহত্যার নির্দেশ দিয়েছিল, তাদের নাম-সাকিন
পাওয়া গেছে । নামের তালিকা বিশাল । তালিকায় খুঁটিনাটি সবই লিখেছে ষড়যন্ত্রকারী যুবক-যুবতীরা ।
আমি লিখতে বসে এই তালিকার উপযুক্ত নাম খুঁজে পাচ্ছিলুম না । তখনই কাজলের প্রস্তাবটা পেলুম ।
তালিকাটার নাম দিলুম ‘ভণ্ডকোষ’ ।
মানে বেশ সহজ । গণহত্যা যারা করিয়েছিল আর যারা উদ্বাস্তদের মরিচঝাঁপিতে বসবাসের জন্য ডেকে এনেছিল,
তারা ছিল ভণ্ড ; তাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল উদ্বাস্তুদের ভোট পাওয়া । উদ্বাস্তুদের ভোটে তারা ক্ষমতা দখল করে
লোকগুলোকে ভুলে যায়, এমনকি তাদের নিকেশ করার প্যাঁচও কষে ফ্যালে । সেই রাজনৈতিক নেতা আর ক্যাডারদের
সঙ্গে মিলিয়ে নেয়া যাক বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত চরিত্র মুরারী শীলকে । কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্যের
একটি ব্যতিক্রমী অসাধারণ চরিত্র মুরারী শীল। মুরারী চরিত্রের বাস্তবতা কবিকঙ্কণকে আধুনিক সাহিত্যের প্রবেশপথের
সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। কারণ উপন্যাসে যে বস্তুনিষ্ঠ নিরপেক্ষ সজীব চরিত্র চিত্রণের দায়বদ্ধতা থাকে ঔপন্যাসিকের,
সেই দায়বদ্ধতা নিয়ে মুকুন্দরাম গড়েছিলেন মুরারী শীল চরিত্রকে।
বর্তমান কালখণ্ডে আমাদের অনেকের কাছে, দৈনন্দিন কথোপকথনের একটি বিশাল অংশ গসিপ বা আড্ডার
চারপাশে আবর্তিত হয়। আমরা বন্ধু, পরিবার-সদস্য আর বিখ্যাত লোকেদের ন্যাকামি আর ভুল
বা কাজ সম্পর্কে কথা বলতে ভালোবাসি। তার উপরে, সংবাদ সংস্থা আর সামাজিক নেটওয়ার্কগুলোর কারণে
আমাদের গ্যাঁজানোর ব্যাপারটা পরিবর্ধকক্রিয়া হয়ে দাঁড়ায় । আমরা সবাই খবর পড়ে লোকেদের বদনাম করতে
অভ্যস্ত, বিশেষত যখন তা রাজনীতিবিদ বা অভিনয়শিল্পীদের নিয়ে হয়। কিন্তু একটি বিশেষ শব্দ আছে যা
সত্যিই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যদি কাউকে বদনাম করতে হয় তবে তাকে "ভণ্ড" বলে-বলে প্রচার করলেই হলো ।
ভণ্ডামি শব্দটা সাধারণত অন্যদের অনৈতিক কাজের সমালোচনা বা নিন্দা করার জন্য ব্যবহৃত হয় অথচ
অনেল সময়ে যিনি আরোপ করছেন তিনি নিজেই সেই কাজগুলোতে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন । ব্যাপারটা
আরোপকারীকে সেই অনৈতিক কাজে লিপ্ত হওয়ার চেয়েও খারাপ করে তুলতে পারে, কিন্তু আরোপকারী
মোটেও নিজের সমালোচনা করে না । ভণ্ডামির মনোবিজ্ঞানে ডুব দিলে ব্যাপারটা খোলোশা হতে পারে।
আমাদের সবারই ভণ্ডের মতন আচরণ করার সবচেয়ে সুস্পষ্ট কারণ হল স্বার্থ। যখন মানুষকে প্রশ্ন করা হয়
যে কেন তারা তাদের নিজস্ব নৈতিক মানগুলির সাথে পরস্পরবিরোধী আচরণ করছে, তখন অনেকেই বলবেন
যে ব্যক্তিগত ক্ষতি নৈতিকভাবে কাজ করার অভিপ্রায়কে ছাড়িয়ে যাচ্ছে বলে করছেন । মূলত, আমরা প্রত্যেকেই
ন্যায্য আচরণ করতে চাই যতক্ষণ না আমরা ঘটনাটায় জড়িয়ে পড়ি আর আমাদের নিজস্ব ব্যক্তিগত পরিণতির
সম্মুখীন হই।
আমরা প্রত্যেকেই ন্যায্য আচরণ করতে চাই যতক্ষণ না আমরা নিজে জড়িয়ে পড়ি, যেমন বাড়ির অভিভাবকদের
নিষেধ থাকে বলে কম বয়সে অনেকে মদ-গাঁজা খেয়ে চেপে যান কিংবা যৌবনে কয়েকজন নারীর সঙ্গে সম্পর্ক
পাতিয়ে চেষ্টা করেন যে কেউই যেন অন্য প্রেমিকাদের সম্পর্কে জানতে না পারে । আসলে ভণ্ডামি হল পুণ্য বা
সাধুচরিত্রের এমন মিথ্যার বহিঃপ্রকাশ, যেখানে ধর্ম বা নৈতিকতার সাপেক্ষে আসল চরিত্র বা প্রবৃত্তিকে গোপন রাখা
হয়। সাধারণ অর্থে মিথ্যা, কপটতা, কৃত্রিমতা এসবকে ভণ্ডামি বলে মনে করা হয়। এ এমন একটি কাজ যেখানে
কেউ এমন আচরণ করে অন্যে যার নিন্দা করে। মনোবিজ্ঞানে এটি নিজের বলা নৈতিক নিয়ম নীতি মান্য
করার ব্যর্থতা । ব্রিটিশ রাজনৈতিক দার্শনিক ডেভিড রান্সিম্যান-এর মতে,"আরও অন্যান্য রকমের ভণ্ডামির মধ্যে রয়েছে
নিজে কোন কিছু না জেনেও তা জানার ভান করা ।”
লোকে ভণ্ডামি করে কেননা তা তাদের সাহায্য করে, এটা নিশ্চিত। কিন্তু আমরা ব্যাপারটা আমাদের সম্পর্কের
ক্ষেত্রেও ব্যবহার করি। বেশিরভাগ সময়ে, যখন আমরা অন্য কারোর কাজের ন্যায্যতা বা নৈতিকতাকে মূল্যায়ন করি,
তখন আমরা তাদের কঠোরভাবে বিচার করি। অথচ নিজেরা সেই কাজ করে ততো কঠোরভাবে বিচার করি না ।
মজার ব্যাপার হল, অন্যদের ব্যাপারে আমাদের রায় অনেক বেশি অনুকূল হতে পারে যদি অন্যরা আমাদের দলের হয় ।
আমরা প্রায়শই নিজের গোষ্ঠীর সদস্যের ভণ্ডামিকে আমাদের নিজের মতো ন্যায্য বলে বিচার করি। আমরা অন্য
গোষ্ঠীর মানুষের ভণ্ড আচরণের জন্য আরও বেশি ঘৃণা করি, যখন সেই লোকেরা একটি সামাজিক বৃত্তের বাইরে
পড়ে যে সামাজিক বৃত্ত নিজেরা এঁকেছি ।
একটু আগেই মরিচঝাঁপির কথা বলেছি । দেখা গেছে যে যাঁরা ভুলিয়ে-ভালিয়ে উদ্বাস্তুদের ডেকে এনেছিলেন,
তাঁরা প্রত্যেকে অস্বীকার করেছেন । যাঁরা গণহত্যার জন্য দায়ি তাঁরা বলেছেন দু-একজন মারা গিয়েছিল ।
দীপ হালদার তাঁর ‘ব্লাড আইল্যাণ্ড’ বইতে কয়েকজনের সাক্ষাৎকার একত্রিত করেছেন, যাঁরা দণ্ডকারণ্য থেকে
মরিচঝাঁপিতে এসেছিলেন তাঁদের এবং যাঁরা সেই সময়ে সরকারি দায়িত্বে ছিলেন তাঁদের । যাঁরা দণ্ডকারণ্য থেকে
মরিচঝাঁপি দ্বীপে বসতি গড়ে ছিলেন আর মুখ্য মন্ত্রী যখন বললেন “এদের মেরে তাড়াও” তখন সরকারের পক্ষের
পুলিশ আর নেতারা দ্বীপটাকে চারিদিক থেকে ঘিরে ১৪ থেকে ১৬ মে ১৯৭৯ সালে উদ্বাস্তুদের কচুকাটা করলেন,
যাঁরা ছিলেন নমঃশুদ্র সম্প্রদায়ের । তখনকার আনন্দবাজারে সংবাদ বিস্তারিত প্রকাশ করা হয়নি, তার কারণ
বামপন্হী ক্যাডাররা কর্মীদের প্যাঁদানি দিয়েছিলেন আর সরকার ধমক দিয়ে বলেছিল যে তাদের বিরুদ্ধে খবর
ছাপলে বিজ্ঞাপন বন্ধ করে দেয়া হবে । দীপ হালদারকে ‘অপারেশন মরিচঝাঁপি’র পুলিশ সুপার অমিয়কুমার সামন্ত
ফোনে জানিয়েছিলেন যে কেবল একজন আদিবাসী বউ মারা গিয়েছিল । দীপ হালদারকে তখনকার সুন্দরবন
মন্ত্রী কান্তি গাঙ্গুলি বলেছিলেন যে ওরা সবাই উদ্বাস্তু ছিল না, আশ-পাশ থেকে আসা জমি দখলকারী ছিল,
তাও পাঁচ-ছয়জন মারা গিয়েছিল কিনা সন্দেহ । মরিচঝাঁপি নিয়ে এতো কথা বললুম কেন ? বললুম যাতে ভণ্ডামি
বা কপটতা ব্যাপারটা যাতে বুঝতে সুবিধা হয়।
কিন্তু ভণ্ডামি বা কপটতা এত ঘৃণ্য কেন? একটি শক্তিশালী ব্যাখ্যা মেলে যা মিথ্যা সংকেত সম্পর্কিত।
বস্তুত ভণ্ডরা তাদের অনৈতিক কাজে প্রতারণার দুটি স্তর তৈরি করে---মামুলি মিথ্যাবাদীদের তুলনায় আরেকটি
স্তর। মামুলি মিথ্যাবাদীরা কেবল বলে যে তারা নৈতিকভাবে কাজ করেছে, যদিও আদপে তারা তা করেনি।
দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তারা কাজটা করেছে বলে স্বীকার করে না । মরিচঝাঁপির ক্ষেত্রে আমরা দেখলুম পুলিশ সুপার আর
মন্ত্রী কিছুই স্বীকার করতে চাইলেন না । আসলে কেউ যখন কপটভাবে কারও অনৈতিক আচরণের নিন্দা করে না,
তখন তারা ব্যক্তিগত দুর্ব্যবহার, মিথ্যা, প্ররোচনা বা কারসাজিকে নানা ছুতোনাতায় আড়াল করে।
ছেলেমেয়ের মিথ্যা কথাকে মা-বাবা ধরে ফেলেন, সেটা মামুলি মিথ্যা, তা ভণ্ডামি নয় । সেই ছেলে-মেয়ে বড়ো হয়ে
যখন মদ-গাঁজা খেয়ে, তার গন্ধ সত্বেও বলে যে, অমুককে জিগ্যেস করো, আমি খাইনি, তখন ভণ্ডামি করে,
সে অমুককেও তার ভণ্ডামির অংশীদার করে তোলে । তার মানে নিছক মিথ্যাবাদীদের আমরা সহ্য করতে পারি
কিন্তু ভণ্ড বা কপটদের সহ্য করতে পারি না । এই ব্যাপারটা ভণ্ডরা জানে, তাই তারা ঘটনাগুলো এমন মুখ করে
বলবে যাতে শ্রোতার মনে হয় সে সত্যি কথাই বলছে ; তারা মুখোশ পরে এমন চেষ্টা করে যাতে কোনও ভুল
সংকেত না যায় ।
দেশভাগের কালখণ্ডের মতন মঙ্গলকাব্যগুলো বাংলার ইতিহাসের এক ক্রান্তিকালের ভাষ্য। ওই সময়টায় বাংলার
রাষ্ট্র-সমাজ নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে একটা জটিলতার ঘূর্ণাবর্তে উপনীত। এ জটিলতার প্রভাব সমাজ-সংস্কৃতির
ওপর তো বটেই, মানুষের ওপরও বর্তেছে। কাজেই সে সময়কার সাহিত্যে বর্ণিত বিভিন্ন চরিত্রে সমকালীন জীবনের
একটা সংলগ্নতাকে কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না, এমনকি সে চরিত্র যদি পৌরাণিক বা ধর্মাশ্রিতও হয় তবুও।
পর্যবেক্ষণের সূক্ষ্ম ক্ষমতা ছিল বলেই মুকুন্দরাম বাঙালির তখনকার সমাজ থেকে, মরিচঝাঁপির গণহত্যাকারীদের
মতনই, মুরারী শীল চরিত্রটিকে সাহিত্যে তুলে আনতে পেরেছেন। মুরারীকে ষোড়শ শতকের সমাজ পরিবেশে খুঁজলে
যেমন পাওয়া যেতো, তেমনি মরিচঝাঁপির ঘটনার পরও পাওয়া যাবে আমাদের দেশে । মানুষ যে কত ভণ্ড, শঠ,
লোভী আর স্বার্থপর হতে পারে তার পরিচয় পাওয়া যায় মুরারী শীলের চরিত্রে। মুরারী শীল তো কবিকল্পিত ।
বাস্তবজগতের ভণ্ডগুলো আরও বজ্জাত, ক্ষতিকর, গণকলঙ্ক। আমার অনেক আশা ছিল পশ্চিমবঙ্গের বামপন্হীদের নিয়ে ।
ভাবিনি যে তারাও শেষকালে একদল ভণ্ডের ভূমিকায় নামবে ।
হিন্দিতে ভণ্ডকে বলা হয় পাখণ্ড । আমি শৈশব থেকে হিন্দিভাষী এলাকায় ছিলুম বলে শব্দটার সঙ্গে পরিচিত।
ইংরেজিতে হিপোক্রিট বললে কিন্তু মানুষটার ভণ্ডামি বা পাখণ্ডিপনা ধরা পড়ে না । জানি না ইংরেজিতে একজন
ভণ্ডকে কী বলা হবে ! পাখণ্ড মানে একজন ভণ্ড ;এমন কাজ করে যা আত্মতৃপ্তির জন্য । সে নিজেকে মহান বলে
দাবী করে । সমাজকে বিভ্রান্ত করে, তাকে কপটতা বলে। যে অন্যকে প্রতারিত করার জন্য ভক্তি বা উপাসনা
করার ভান করে। পাখণ্ড মানে যে বেদকে অস্বীকার করে বা নিন্দা করে, যে বেদে বিশ্বাস করে না, যে সর্বদা
অ-বৈদিক কাজ করে, তাকে পাখণ্ড বলা হয়। বাংলা অভিধানে ভণ্ড শব্দের তিনটি মানে দেয়া আছে : একটা হল
নষ্ট, বিপর্যস্ত, লণ্ডভণ্ড, ভণ্ডুল করা । দ্বিতীয়টি হল কপট, ভানকারী, ছদ্ম (ভণ্ড সন্ন্যাসী), শঠ, প্রতারক। তৃতীয়
হল ভাঁড়ানো বা ভণ্ডানো, ঠকানো, প্রতারণা করা, ভাঁড়ানো।
সাহিত্যিকরা বহু ভণ্ড চরিত্রের রূপায়ণ করে গেছেন ; তাদের মধ্যে পাওয়া যাবে মুরারী শীলদের । ইলিয়ড-ওডিসি,
মহাভারত-রামায়ণ মহাকাব্যে ভণ্ড চরিত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। গ্রিক মিথে রয়েছে দেব-দেবীর বিচিত্র ভণ্ডামির বিবরণ।
মহাভারতের শকুনি একটি ভণ্ড চরিত্র। জন মিল্টনের প্যারাডাইস লস্টের শয়তান চরিত্রটি ভণ্ড , বেউলফের গ্র্যান্ডেলের
মা প্রকৃত ভণ্ড। রবীন্দ্রনাথ ভণ্ড চরিত্র হিসেবে শেক্সপিয়রের ফলস্টাফের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, কল্পনার
রসে জারিত হয়ে চরিত্রগুলো সৃষ্টি হয়েছে বলে ভণ্ড হয়েও আমাদের মনে সেগুলো দাগ কাটে। 'ওথেলো'র ইয়াগো
মতলববাজ, ধূর্ত চক্রান্তকারী। হ্যামলেটের কাকা ক্লডিয়াস ভণ্ডামির পরিচয় দিয়েছে কুকাজ করে। সে খুন করে নিজ ভাই
তথা হ্যামলেটের বাবাকে, বিয়ে করে রানি গারট্রুডকে, যাকে হ্যামলেট মা বলে ডাকে। বাবার প্রেতাত্মা হ্যামেলেটের
কাকাকে বলেছে বজ্জাত, বলেছে চতুর, ব্যভিচারী, পশু, বিশ্বাসঘাতক। 'টেম্পেস্টে' কুচক্রী অ্যান্টোনিও প্রস্পেরোকে
সরিয়ে মিলানের ডিউক হয়েছে। মার্চেন্ট অব ভেনিসের শাইলক ক্রূরতায় ভণ্ডামি করেছে। কিং লিয়ার, রিচার্ড দ্য থার্ডে
ভণ্ড চরিত্র আছে। জোশেফ কনরাডের উপন্যাসে, ক্রিস্টোফার মার্লোর নাটকে, হার্ডির টেসে, নবকভের ললিতায়,
মেলভিনের মবিডিকে স্মরণীয় হয়ে আছে নানা ভণ্ড চরিত্র । কিপলিংয়ের শের খানের ভণ্ডামি ছাড়াও জর্জ অরওয়েলের
১৯৮৪-তে, ডিকেন্সের রচনায়, গোর্কি ও হামসুনের উপন্যাসে চরিত্রের ভণ্ডামি আমাদের পরিচিত। বর্তমানে
কিশোর সাহিত্য হ্যারি পটার সিরিজের উপন্যাসগুলোয় জে কে রাউলিং ভণ্ডদের বহুমাত্রিকতা তুলে ধরেছেন।
বিশ্বসাহিত্যের ভণ্ড চরিত্রগুলোকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এরা কেউ অপরাধী, খারাপ ব্যক্তি, সংকীর্ণমনা,
অসততায় অসামান্য আর নায়কের বিপরীতে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শক্তিশালী। সাধারণ মানুষের কাছে এরা বাজে লোক,
শত্রু, হৃদয়হীন, নিষ্ঠুর নীতিহীন। সাহিত্যে ভণ্ড চরিত্রের রূপায়ণের সার্থকতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :
'বহু লোকের বহুবিধ মন্দত্বের খণ্ড খণ্ড পরিচয় সংসারে আমাদের কাছে ক্ষণে ক্ষণে এসে পড়ে; তারা আসে, তারা যায়,
তারা আঘাত করে, নানা ঘটনায় চাপা প'ড়ে তারা অগোচর হতে থাকে। সাহিত্যে তারা সংহত আকারে ঐক্য লাভ
করে আমাদের নিত্যমনের সামগ্রী হয়ে ওঠে, তখন তাদের আর ভুলতে পারি নে।'
রামনারায়ণ তর্করত্ন তাঁর নাটক ‘কুলীনকুল সর্বস্ব’ (১৮৫৪)তে দেখিয়েছিলেন সেই সময়ের ব্রাহ্মণদের মধ্যে কেমন
ভণ্ডরা ছিল । তখনকার বাংলাদেশে কৌলীন্য প্রথার ফলে মেয়েদের কেমন দুরবস্থায় পড়তে হতো আর কুলীন
পাত্ররা কেমন ব্যভিচার ও নীচতার পরিচয় দিতো ঘটকদের ভণ্ডামিতে কন্যাদায়গ্রস্ত বাবারা সর্বস্বান্ত ও শোকে
আক্রান্ত হতেন । এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য মন্বন্তরের পটভূমিতে লেখা তুলসী লাহিড়ীর লিখেছিলেন তাঁর নাটক ‘ছেঁড়া তার’ ( ১৯৫০ )। এই নাটকের কাহিনি
কৃষক জীবনাশ্রিত এবং তা উত্তরবঙ্গের রংপুর জেলাকে ভিত্তি করে কেন্দ্রীভূত । এ নাটকে দুটি বিরুদ্ধ পক্ষের সৃষ্টি
করা হয়েছে।এক পক্ষে ভণ্ড ও নিপীড়ক হিসেবে আছে হাকিমুদ্দি আর অত্যাচারিত সংগ্রামী মানুষের মুখপাত্র হিসেবে
আছে রহিমুদ্দী। এই দৃষ্টিতে বিচার করলে দেখা যাবে এ নাটক ভণ্ড হাকিমুদ্দী বনাম সৎ রহিমুদ্দীর বিরোধ।
এই বিরোধের একদিকের ফলাফল হোল সমবেত ও ঐক্যবদ্ধ জনগণের কাছে হাকিমুদ্দীর পরাভব ও শাস্তিভোগ;
অপর পর্যায়ের ফল— রহিমুদ্দীরই পরাভব, তার আত্মহত্যা। উল্লেখ করতে হয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সাজাহান (১৯০৯)
নাটক যাতে রয়েছে কপটতার বিশেষ উদাহরণ ঔরঙ্গজেব ; ভারত সিংহসন ঘিরে যে রাজনৈতিক চক্রান্ত ও ভ্রাতৃঘাতী
সংগ্রামের রক্তাক্ত পটভূমিকা রচিত হয়েছিল, নাট্যকার তাকে জীবন্ত করে তুলেছেন। ভারত ইতিহাসের সেই দুর্যোগময়
পটভূমিকায় নায়ক নায়িকার অন্তর্জীবনের কাহিনি যুক্ত করে নাট্যকার মানবজীবনেরই রহস্য উদ্ঘাটন করেছেন।
দুর্গে বন্দি সাজাহানের দ্বন্দ্ব বিড়ম্বিত মর্মান্তিক পরিণতি, কূটকৌশলী ঔরঙ্গজেবের জটিল চরিত্র, মদ্যপায়ী নির্বোধ,
বিলাসপ্রিয় সুজা, উদার হৃদয় দারা, ব্যক্তিত্বময়ী তেজস্বিনী জাহানারা,লঘু চপল পিয়ারা, কর্তব্যনিষ্ট মোহম্মদ,
প্রভৃতি চরিত্র স্বমহিমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। দিলদার নাট্যকারের বিশিষ্ট সৃষ্টি। সব মিলিয়ে মুঘল যুগের ঐশ্বর্য ও
রক্তাক্ত লোভের সংঘাতময় পটভূমিকায় মানুষের প্রবৃত্তিধর্ম ব্যক্তি চরিত্র এখানে বিশেষ ভাবে অঙ্কিত হয়েছে।
বিশেষ করে উল্লেখ করতে হয় মাইকেল মধুসূদন দত্তের নাটক ‘বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ’ (১৮৬০)। এই নাটকে
দেখানো হয়েছে, ভক্তপ্রসাদ একজন ভণ্ড জমিদার, গরীব চাষীর এক পয়সা খাজনা মুকুব করে না। অথচ সে পরম
রসিক। পরস্ত্রীর রূপ বর্ণনা শুনলে ভাববিহ্বল হয়ে ভারতচন্দ্রের কবিতা আবৃত্তি করে। হানিফের স্ত্রী ফতিমার কাছে
দূত পাঠিয়ে তাঁর অভিসারকে নিশ্চিত করে। ভণ্ডটি যাবতীয় কুকর্মে রত, অথচ সে-ই আবার নিজের ছেলের
ধর্মাচরণের প্রতি বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখে । যে লোকটা মুসলমান নারীর সঙ্গে শোয় সেই আবার মুসলমানের ছোঁয়া
খাবার খেতে আতঙ্কগ্রস্ত। এই সমস্ত নাটক দেখে বা পড়ে বলা যায় যে বাঙালির সমাজে ভণ্ডরা ছিল, আছে এবং
চিরকাল থাকবে ।
 গোবিন্দ ধর | 122.179.172.247 | ৩০ আগস্ট ২০২১ ১২:৪৫734913
গোবিন্দ ধর | 122.179.172.247 | ৩০ আগস্ট ২০২১ ১২:৪৫734913-
মলয় রায়চৌধুরীর মুখোমুখি গোবিন্দ ধর
গোবিন্দ : আপনি প্রচুর সাক্ষাৎকার দিয়েছেন । দুটি সংকলন আছে আপনার সাক্ষাৎকারের। কিন্তু বেশিরভাগ প্রশ্নকর্তা হাংরি আন্দোলন সম্পর্কে প্রশ্ন করেছেন । আপনার জীবন ও গ্রন্হাবলী নিয়ে বিশেষ প্রশ্ন কেউ করেননি । আমি সেই ধরনের প্রশ্ন করতে চাই, যা অন্যেরা করেনি । আপনার শৈশব কেটেছে পাটনার ইমলিতলা নামে এক অন্ত্যজ বস্তিতে, সেখানে কৈশোরে কুলসুম আপা নামের এক কিশোরীর সঙ্গে আপনার জীবনে যৌনতার প্রথম পরিচয় । তা কি প্রেম ছিল ? আপনার ধর্মনিরপেক্ষতার বীজ হিসাবে কি কাজ করেছিল ঘটনাটা ?
মলয় : না, তা প্রেম ছিল না । উনি আমাকে গালিব আর ফয়েজের কবিতার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন আর নিজেই এগিয়ে এসে সংসর্গ পাতিয়েছিলেন । ইমলিতলা পাড়া ছিল চোর,ডাকাত, পকেটমার অধ্যুষিত গরিবদের পাড়া, তাদের বাড়িতে অবাধে ঢুকে পড়া যেতো । কুলসুম আপাদের বাড়িতেও, এমনকী ওদের মসজিদের ভেতরেও খেলা করার সময়ে ঢুকে লুকিয়েছি । এখন ভারতীয় সমাজ এমন স্তরে পৌঁছেচে যে অমন বাল্যকাল অভাবনীয় মনে হবে । আমার ধর্মনিরপেক্ষতা বা ব্যাপারটাকে যা-ই বলো, ওই পাড়াতেই সূচিত হয়েছিল । দাদা সমীর রায়চৌধুরী এই অভিজ্ঞতাকে বলেছেন একলেকটিক । রামমোহন রায় সেমিনারি ব্রাহ্ম স্কুলে পড়ার সময়ে আমার ক্রাশ ছিলেন গ্রন্হাগারিক নমিতা চক্রবর্তী, যাঁর প্রভাবে আমি মার্কসবাদে আকৃষ্ট হয়েছিলুম । আমার ‘রাহুকেতু’ উপন্যাসে এনার নাম সুমিতা চক্রবর্তী ।
গোবিন্দ : সেই পাড়ায় আপনারা নাকি পোড়া ইঁদুর, শুয়োরের মাংস, ছাগলের নাড়িভূঁড়ির কাবাব, তাড়ি, দিশি মদ, গাঁজা ইত্যাদি খেতেন । বাড়িতে তার জন্য পিটুনি খেতেন না ?
মলয় : দাদা বলতো বাড়িতে বলবি না, মৌরি খেয়ে নে । কিন্তু মুখে গন্ধ শুঁকে মা টের পেয়ে যেতেন আর বকুনি দিতেন । কিন্তু পাড়ার লোকেদের টানে আবার অমন কাণ্ড করতুম । এই সমস্ত কারণে দাদা ম্যাট্রিক পাশ করার পর বাবা ওনাকে কলকাতা সিটি কলেজে ভর্তি করে দিয়েছিলেন আর নিজে একটা ঝোপড়ি কিনে দরিয়াপুর নামে পাড়ায় বাড়ি করেন। আমি সেই বাড়িতে একা থাকতুম । আমার বাল্যস্মৃতি ‘ছোটোলোকের ছোটোবেলা’ আর ‘ছোটোলোকের যুববেলা’ পড়লে জানতে পারবে নানা ঘটনা । সিটি কলেজে দাদার সহপাঠী ছিলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় । চাইবাসা আর ডালটনগঞ্জে দাদা মৎস্য বিভাগে পোস্টেড থাকার সময়ে প্রচুর মহুয়ার মদ খেয়েছি। দাদা হরিণের মাংস খাবারও ব্যবস্হা করে দিতেন । কতো রকমের মাছ যে খেয়েছি তার ইয়ত্তা নেই ; গেঁড়ি-গুগলির বিরিয়ানিও খেয়েছি ।
গোবিন্দ: : আপনারা হাংরিরা শুনেছি যৌনকর্মীদের পাড়ায় যেতেন । কৃত্তিবাসের কবি-লেখকরাও যেতেন অথচ তা স্বীকার করেননি নিজেদের জীবনীতে । আপনার অভিজ্ঞতার কথা বলুন । বিদেশে গিয়ে যৌনকর্মীদের পাড়ায় গেছেন ?
মলয় : না, কেবল সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন, হাংরি বুলেটিনে । আমার পিসেমশায় যাওয়া আরম্ভ করেন । ওনার দেখাদেখি ওনার বড়ো ছেলে অজয় বা সেন্টুদা ঢুঁ মারা আরম্ভ করেন । সেন্টুদা আমাকে ওই পাড়ার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন । দুপুর বেলায় রেট কম থাকে বলে সেন্টুদা দুপুরে আমাকে নিয়ে যেতেন । হাংরিদের মধ্যে শৈলেশ্বর ঘোষ, বাসুদেব দাশগুপ্ত, অবনী ধর রেগুলার যেতো, প্রৌঢ় বয়সেও, ওদের পরস্পরের চিঠিতে পাবে ওদের প্রিয় যৌনকর্মী বেবি, মীরা, দীপ্তির নাম । সবচেয়ে ভীতিকর হল কোনও যৌনকর্মীর প্রেমে পড়া। এখন তো আলো ঝলমলে অন্য চেহারা নিয়ে ফেলেছে এলাকাটা । আধুনিকা যৌনকর্মীরা জিনস-স্কার্ট পরে রাস্তার মাঝখানেই দাঁড়িয়ে থাকেন, স্টাইলে সিগারেট ফোঁকেন । বিদেশে গিয়ে যৌনকর্মীদের পাড়ায় গিয়ে দেখে বেড়িয়েছি কিন্তু কারোর সঙ্গে শুইনি কেননা যৌনরোগকে আমার ভীষণ ভয় । বোদলেয়ারের জীবনী পড়ে আরও আতঙ্কিত হই । বিদেশিনীদের কাছে সারা পৃথিবী থেকে খদ্দেররা যায় । ভিয়েৎনামের যুদ্ধের কারণে থাইল্যাণ্ড হয়ে গিয়েছিল যৌনকর্মীদের বিরাট বাজার ; কাঁচের দেয়ালের ওইদিকে মেয়েরা বুক খুলে আর জাঙিয়া পরে খদ্দের ডাকতো । আমস্টারডামে একটা পাড়া ছিল যার গলিগুলোতে বিশাল কাচের জানলার সামনে প্রায় উলঙ্গ মেয়েরা ফিকে লাল আলোয় বসে থাকতো আর নীল আলো জ্বললে বুঝতে হতো সমকামীদের ডাকছে ।
গোবিন্দ : আপনার আত্মজীবনীতে এসব এসেছে ?
মলয় : হ্যাঁ, ‘ছোটোলোকের শেষবেলা’তে এসেছে । তাছাড়া ‘রাহুকেতু’ উপন্যাসে আমি ওই সময়ের সবাইকে আর ঘটনাগুলোকে তুলে এনেছি । উপন্যাসটা প্রতিভাস প্রকাশিত ‘তিনটি নষ্ট উপন্যাস-এর অন্তর্ভুক্ত । মামলার সময়ে আমার শরীর হঠাৎ খারাপ হয়ে যেতে পাটনায় ফিরে গিয়েছিলুম আর আমাদের পারিবারিক ডাক্তার অক্ষয় গুপ্ত সংবাদপত্র পড়ে ধরে নিয়েছিলেন যে আমার যৌনরোগ হয়েছে আর বরাদ্দ করেছিলেন পেনিসিলিন ইনজেকশান । জানতে পেরে পরের দিনই কমপাউণ্ডারকে বলেছিলুম, আর দিতে হবে না, ও-রোগ আমার হয়নি ।
গোবিন্দ : অর্থাৎ আপনি গ্রামের মানুষ নন, শহরের মানুষ । তবু আপনার উপন্যাসে, যেমন ডুবজলে যেটুকু প্রশ্বাস, নামগন্ধ, জলাঞ্জলি, ঔরস ইত্যাদি উপন্যাসে গ্রাম এসেছে বিপুলভাবে । কেমন করে আপনি বর্ণনাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুললেন ? ঔরস উপন্যাসে আপনি অবুঝমাঢ়ের মাওবাদী এলাকা ডিটেলে বর্ণনা করেছেন ।
মলয় : চাকুরিসূত্রে সারা ভারতের গ্রামগঞ্জ ঘুরেছি, চাষি, তাঁতি, জেলে, কামার, কুমোর, খেতমজুর, নৌকোর ছুতোর আর নিম্নবর্ণের মানুষের সাক্ষাৎকার নিয়েছি ক্ষেত্রসমীক্ষায় । অধিকাংশ চরিত্র পেয়েছি সমীক্ষার সময়ে । যখন রিজার্ভ ব্যাঙ্কে চাকুরি করতুম তখন সহকর্মীদের গ্রামে গেছি । রিজার্ভ ব্যাঙ্কের চাকরিটা ছেড়ে এআরডিসিতে গেলুম, সেখান থেকে নাবার্ড। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের চাকুরিটা ছেড়েছিলুম গ্রামের জীবন আর মানুষ দেখার লোভে । এখন তো আমার যা পেনশন তার চেয়ে বেশি পেনশন পায় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পিওন । তবে প্রচুর ঘোরাঘুরি করেছিলুম তখন। পশ্চিমবাংলায় সিপিএমের ভয়ে অনেকে কথা বলতে চাইতো না বলে দাড়ি বাড়িয়ে অবাঙালি এম আর চৌধারী হয়ে গিয়েছিলুম, হিন্দিতে কথা বলতুম ।
গোবিন্দ : কোনও বিশেষ কোন স্মৃতি?
মলয় : প্রচুর স্মৃতি জমে আছে, লিখেছিও কিছু-কিছু । সবচেয়ে বিস্ময়কর হলো হিমালয়ের তরাইতে খাঁটি ভারতীয় গরু আছে কিনা তার তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে এক মরা বাঘিনীর স্মৃতি, যার রক্তাক্ত যোনিও আকর্ষণ করেছিল । স্হানীয় লোকেরা, সকলেই হিন্দু, বাঘিনীর মাংস-হাড় ইত্যাদি সংগ্রহের জন্যে কাড়াকাড়ি করেছিল। একজন আমাকে আর আমার সহকর্মীকে রেঁধে খাইয়েছিল । ইঁদুর খেয়েছি শৈশবে, বাঘ খেলুম যৌবনে । ঘোরাঘুরির চাকরির আগে জানতুম না কতোরকমের গরু, ছাগল, শুয়োর, মুর্গি, হাঁস, চাল, আলু ইত্যাদি হয়। জলসেচের কতোরকমের ব্যবস্হা আছে আর কোন ফসলে কখন কীরকম জলসেচের দরকার হয় কিছুই জানতুম না।
গোবিন্দ : কলকাতায় কবিদের কাছে খালাসিটোলার এতো নামডাক । আপনি যেতেন ?
মলয় : ওখানেও প্রথমবার গেছি সেন্টুদার সঙ্গে । পরে লেখক বন্ধুদের সঙ্গে । অবনী ধর একটা টেবিলে উঠে জীবনানন্দের জন্মদিনে নেচেছিল, সেটা ‘অমৃত’ পত্রিকায় আর ‘দি স্টেটসম্যান’ সংবাদপত্রে খবর হয়েছিল । ক্লিন্টন বি সিলি ওনার জীবনানন্দ বিষয়ক ‘এ পোয়েট অ্যাপার্ট’ বইতে ঘটনাটার উল্লেখ করেছেন । তখনকার দিনে খালাসিটোলার বাইরে গাঁজা-চরস-আফিমের একটা সরকারি দোকান ছিল ; সেখান থেকে একটা পুরিয়া কিনে এগোতেই কমলকুমার মজুমদারের সামনাসামনি হই ; টাকার টানাটানি আর মামলার খরচ জানতে পেরে উনি আমাকে একটা একশো টাকার নোট দিয়েছিলেন। সুভাষ ঘোষ অবশ্য খালাসিটোলার বদলে পছন্দ করতো সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউতে ‘অম্বর’ বার ।
গোবিন্দ : আপনি জীবনী লিখেছেন বা জীবন ও শিল্প বিশ্লেষণ করেছেন এবং অনুবাদ করেছেন বোদলেয়ার, র্যাঁবো, অ্যালেন গিন্সবার্গ, পল ভেরলেন, সালভাদোর দালি, পল গঁগা, জাঁ জেনে, মায়াকভস্কি, জীবনানন্দ দাশ, নজরুল ইসলাম, দস্তয়েভস্কি, জাঁ-লুক গোদার প্রমুখের । মনে হয় আপনি যেন এঁদের প্রতি আকৃষ্ট, আপনার জীবন ও চরিত্র ও লেখালিখির সঙ্গে এনাদের মিল আছে বলে ? তা কি স্বীকার করেন ?
মলয় : এটা ঠিক যে এনারা আমাকে আকর্ষণ করেছেন । বোদলেয়ারের আর জীবনানন্দের মতন আমিও একজন পথচর, যদিও করোনা ভাইরাসের কারণে আজকাল আর বেরোই না, কিন্তু আমি জেমস জয়েস, মার্সেল প্রুস্ত, হেনরি মিলার, হুলিও কোর্তাজার, ফুয়েন্তেস, শিবনারায়ণ রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, আনা আখমাতোভা, ওসিপ ম্যানডেলস্টাম, পিকাসো, মার্কেজ, সিলভিয়া প্লাথ,মালার্মে, পাবলো নেরুদা, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপক মজুমদার, ফালগুনী রায়, শৈলেশ্বর ঘোষ প্রমুখকে নিয়েও লিখেছি ; এমনকী আমেরিকার রেড ইন্ডিয়ান গল্পকার হায়মেওস্ট স্টর্মকে নিয়েও লিখেছি। শৈলেশ্বর ঘোষ সম্পর্কে আমার প্রবন্ধে কিন্তু গালমন্দ করিনি, যেমনটা উনি আমাকে প্রাণ ভরে দিয়ে গেছেন ।
গোবিন্দ : শৈলেশ্বর ঘোষ যে হাংরি রচনা সংকলিত করেছেন তা থেকে আপনি, দেবী রায়, সুবিমল বসাক, ত্রিদিব মিত্র, আলো মিত্র, করুণানিধান মুখোপাধ্যায়, অনিল করঞ্জাই পমুখদের বাদ দিয়েছেন। আপনিও নাকি ওনাদের বাদ দিয়েছেন ?
মলয় : না, আমি কাউকে আমার সম্পাদিত সংকলন থেকে বাদ দিইনি । বস্তুত হাংরি বুলেটিন আর জেব্রা পত্রিকা ছাড়া আমি কোনও হাংরি সংকলন সম্পাদনা করিনি । আসলে শৈলেশ্বর-সুভাষ আমার মামলায় রাজসাক্ষী হবার দরুন অপরাধবোধে ভুগতেন, এটা কমন ক্রিমিনাল সাইকোলজি।
গোবিন্দ : বাঙালি মহিলা কবিদের প্রতি আপনার পক্ষপাত দেখা যায় । আপনি যশোধরা রায়চৌধুরী, সোনালী চক্রবর্তী, বহতা অংশুমালী মুখোপাধ্যায়, সোনালী মিত্র, জয়িতা ভট্টাচার্য, মিতুল দত্ত, শ্রীদর্শিনী মুখোপাধ্যায়, আসমা অধরা, মুনীরা চৌধুরী প্রমুখের নাম উল্লেখ করেন, কয়েকজনের বইয়ের ভূমিকাও লিখেছেন । তরুণ পুরুষ কবিদের নিয়ে আপনি আশাবাদী নিশ্চয়ই। কিন্তু পিঠ চাপড়ানোর একটা রেওয়াজ চলছে। এতে সাহিত্যের লাভক্ষতি কি তেমন হচ্ছে?
মলয় : পিঠ চাপড়ানি তো ভালোই । আমার মামলার সময়ে পিঠচাপড়ানি পেলে কাজে দিতো । তার বদলে আমি পেয়েছিলুম কেবল টিটকিরি, আক্রমণ, বিদ্বেষ । সংবাদপত্রগুলো যা ইচ্ছে তা-ই লিখতো। বুদ্ধদেব বসু আমার নাম শুনেই আমাকে ওনার দরোজা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন । আবু সয়ীদ আইয়ুব আমার বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটা চিঠি লিখেছিলেন অ্যালেন গিন্সবার্গকে । এমনকী বন্ধুরাও আমাকে অপছন্দ করতো । শৈলেশ্বর ঘোষ মারা যাবার পর ওর শিষ্যরা আমার বিরুদ্ধে লিখে চলেছে । ঢাকায় একটা বই বেরিয়েছে কবি প্রকাশনী থেকে, তাতে মোস্তাফিজ কারিগর আর সৌম্য সরকার নামে দুজন আমাকে আক্রমণ করেছেন, আমার বইপত্র না পড়েই । তরুণরা তো নানা রকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে, নতুন ভাবনা নতুন আঙ্গিক আনার প্রয়াস করছে, যদিও বয়সের কারণে আমি এখন আর পড়ার অবসর পাই না । আমার পছন্দ হলে আমি প্রশংসা করি ; তা অন্যের পছন্দ নাও হতে পারে। মুনীরা চৌধুরীর কবিতা পড়েছ ? অসাধারণ প্রতিমাভাঙনের কাজ আছে ওনার কবিতায়
গোবিন্দ :প্রায় সকল প্রকাশক, লেখক যখন পাঠক-শূন্যতা টের পান তখন কেউ কেউ একেকটি মেলায় কোনও কোনও বইয়ের দ্বিতীয় তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ হওয়ার বিজ্ঞাপন দেন। এটা তাহলে পাঠকশূন্যতা নয় ? নাকি অন্য কোন যাদুবলে একজন লেখক পাঠকপ্রিয় হয়ে ওঠেন? কিংবা একজন প্রকাশক পাঠকের চাহিদা সত্যি সত্যি অগ্রীম ধরে নিতে পারেন?
মলয় : অনেকের বই বিজ্ঞাপনের জোরে বিক্রি হয়, অনেকের বই পাঠকের মুখে-মুখে ছড়িয়ে পড়ে । অনেকের বই আবার সাংস্কৃতিক রাজনীতির কারণে বিক্রি হয় না । প্রকাশককে হুমকি দেয়ায় অনেকের বই আটকে যায়। পাঠকের অভাব আছে বলে আমার মনে হয় না । যাঁরা লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশনা থেকে বই প্রকাশ করেন তাঁদের অসুবিধা হলো কলেজ স্ট্রিটে বিক্রির ব্যবস্হা না থাকা । যাঁরা কলকাতার বাইরে থাকেন তাঁদের তো একেবারে সুযোগ-সুবিধা নেই । তবু তাঁদের প্রকাশ করা বইয়েরও পাঠক আছে । দাদা ‘হাওয়া৪৯’ পত্রিকা প্রকাশ করার সময়ে যে বইগুলো বের করেছিল সেগুলোর ভালোই চাহিদা ছিল । এখন ‘হাওয়া৪৯’ সম্পাদনা করে মুর্শিদ । ও আবিষ্কার প্রকাশনী খুলেছে, ওর বের করা বইগুলো ভালোই বিক্রি হয়, ও বিভিন্ন মেলাতেও অংশ নেয় ।
গোবিন্দ : পারিবারিক কোনও স্মৃতি?
মলয় : আমাদের বসতবাড়ি ছিল হুগলি জেলার উত্তরপাড়ায় । আমরা সাবর্ণ রায়চৌধুরী বলে বাড়ির নাম ছিল সাবর্ণ ভিলা, তিনশো বছরের পুরোনো বাড়ি । অবশ্য আদি নিবাস বলতে হলে লক্ষীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের কথা বলতে হয়, যিনি যশোরে মহারাজা প্রতাপাদিত্যের অমাত্য ছিলেন, মোগলদের কাছ থেকে রায়চৌধুরী উপাধি আর কলকাতার জায়গিরদারি পেয়ে চলে আসেন । সাবর্ণ ভিলা হয়ে গিয়েছিল খণ্ডহর । আমার খুড়তুতো বোন পুটিকে ওর বাবা প্রেমিকের সঙ্গে বিয়ে অনুমোদন না করার দরুন পুটি সবচেয়ে বড়ো ঘরের কড়িকাঠ থেকে ঝুলে আত্মহত্যা করে নিয়েছিল । আর তার পরদিনই ঘরটা তার ওপরের স্ট্রাকচারসহ হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে। বস্তুত ব্যাপারটা ছিল যেন সাবর্ণ ভিলার আত্মহত্যা । পুটির আত্মহত্যা আমি ভুলতে পারিনি । এক্ষুনি তোমাকে পিসেমশায়ের কথা বলছিলুম, উনিও মাঝরাতে আহিরিটোলার বাড়ির ছাদ থেকে লাফিয়ে আত্মহত্যা করেন ; ওনার পকেটের চিরকুটে লেখা ছিল ‘আনন্দ ধারা বহিছে ভূবনে’ । বিশাল বাড়িটা ভাঙাচোরা অবস্হায় থাকার দরুণ বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে দাদার বন্ধুদের পরামর্শে কয়েকজন শিক্ষার্থী মুক্তিযোদ্ধাকে ঠাঁই দিতে সুবিধা হয়েছিল ।
গোবিন্দ : আপনার কলেজ জীবনের গল্প বলুন? তখনকার বিশেষ স্মৃতি?
মলয় : আমি পড়তুম পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে । আইএ পড়ার সময়ে যোগ দিয়েছিলুম ন্যাশানাল ক্যাডেট কোর-এ, বন্দুক-পিস্তল চালানো আর নানা জায়গা দেখার লোভে । থ্রিনটথ্রি আর বাইশ বোরের রাইফেল চালিয়েছি । তখনকার পিস্তলগুলো বেশ ভারি হতো । থ্রিনটথ্রিতে প্রতিবার বুলেট ভরতে হতো, এখন কালাশনিকভ থেকে বুলেট বেরোয় চেপে রাখা পেচ্ছাপের মতন ।
গোবিন্দ :পরিবারের কেউ মুক্তিযুদ্ধের সাথে কোনভাবে যুক্ত ছিলেন?
মলয় : পূর্ব পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসা কবি-লেখকদের আশ্রয় দেয়া আর লুকিয়ে রাখাকে যদি মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে যোগাযোগ মনে করো, তাহলে ছিল ।
গোবিন্দ : আপনার গল্প উপন্যাসে দেশভাগ,মুক্তিযুদ্ধ কিরকম এসেছে?
মলয় : দেশভাগ এসেছে আমার কবিতায়, গল্পে, উপন্যাসে, প্রবন্ধে । ‘নামগন্ধ’ উপন্যাসে পাবে দেশভাগে চলে আসার পর একজন বামপন্হীর দ্রোহ আর শেষ পর্যন্ত তার পরিবর্তন । ‘ঔরস’ উপন্যাসে পাবে ১৯৭১-এর বীরাঙ্গনা আর সন্তানকে কেমনভাবে আশ্রয় দিয়েছিলেন, বিয়ে করেছিলেন এক স্কুল শিক্ষক । ‘নখদন্ত’ কাহিনির পোস্টমডার্ন স্ট্রাকচারে পাবে । বহু কবিতায় পাবে।
গোবিন্দ :আপনার সাহিত্যে দেশ ভাগের প্রভাব কতটুকু?কিংবা এই বিষয়টি কেমন করে আসে?
মলয় : নিজস্ব অভিজ্ঞতা ছাড়া আমি লিখতে পারি না, যদিও চেষ্টা করি । সেজন্য দেশভাগ যেটুকু এসেছে তা দেখে। আমি তো পূর্ববঙ্গের মানুষ নই । পঞ্চাশের দশকে শেয়ালদায় উদ্বাস্তুদের ভয়ঙ্কর অবস্হা নিজের চোখে দেখার দরুনই আমি আর দাদা আন্দোলনের কথা ভেবে ছিলুম । দেশভাগে যে নিম্নবর্ণের উদ্বাস্তুরা এসেছিলেন তাঁদের সঙ্গে মিশেছি হিমালয়ের তরাইতে, মানা ক্যাম্পে, ছত্তিসগঢ় আর মধ্যপ্রদেশে, মোতিহারিতে, মহারাষ্ট্রে । এনারা এসেছেন আমার লেখায় ।
গোবিন্দ :পরিবারের কেউ মুক্তিযুদ্ধের সাথে কোনভাবে যুক্ত ছিলেন?
মলয় : পরিবার বলতে তো বাবা-মা-দাদা আর আমি । কেউই সরাসরি যুক্ত ছিলুম না।
গোবিন্দ :বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে কিংবা মুক্তিযুদ্ধে বাঙালিরা এত আন্তরিক কেন ছিলো?
উত্তর : সিমপল । বাঙালি বলে ।
গোবিন্দ :দেশভাগের ফলে আমাদের বাংলা সাহিত্যের উপর কিরকম প্রভাব পড়ে?
মলয় : আমার মনে হয় সেইভাবে পড়েনি যেমনটা বিশ্বযুদ্ধ, সোভিয়েত শাসন ফেলেছে ইউরোপের লেখায় বা লাতিন আমেরিকার ইতিহাস ফেলেছে স্প্যানিশ সাহিত্যে ।
গোবিন্দ :বাঙালি জাতির জীবনে কাঁটাতার নিশ্চয়ই খণ্ডিত জাতিসত্তার জন্ম দিয়েছে? নাকি এর প্রভাব শুধু শিল্পসাহিত্যেই বাস্তবে কিছুই নয়?
মলয় : বলা কঠিন । বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ ক্রমশ ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন, মূলত সউদি আরব, পাকিস্তান, তুর্কি ইত্যাদি দেশের প্রভাবে । এপার বাংলায় আর ত্রিপুরায় বিজেপি জিতলেও বাঙালিরা সেইভাবে হিন্দুত্বের প্রতি আকৃষ্ট হয়নি । লেখকরা অবশ্য একটা পৃথক মিলক্ষেত্র তৈরি করে রেখেছেন ।
গোবিন্দ :হাংরি উত্থানের দিনগুলোর অর্জন বলুন?
মলয় : আমি আর কী বলব । লেখক-পাঠক হিসাবে এই বিশ্লেষণ তো তোমাদের করা দরকার।
গোবিন্দ: আপনার তো কবিতা লেখে সাহিত্যে হাতেখড়ি। আড্ডার দিনগুলোর কথা শুনবো?
মলয় : না, আমি প্রথমে প্রবন্ধ লেখা আরম্ভ করেছিলুম । আমার ধারাবাহিক গদ্য ‘ইতিহাসের দর্শন’ প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল । তারপর লিখি ‘মার্কসবাদের উত্তরাধিকার’ । এই বিষয়গুলো নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা হতো না । দাদার বন্ধুদের সঙ্গে হতো, দীপক মজুমদার আর সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে । সিপিএম সরকারে আসার পর সুভাষ ঘোষ আর বাসুদেব দাশগুপ্ত রাজনীতিতে আগ্রহী হয় ।
গোবিন্দ :কি করে মনে হলো কবিতার পাশাপাশি গল্প উপন্যাসও আপনার বিষয়?
উত্তর : না, না । উপন্যাস আর গল্প লেখা আরম্ভ করেছি বেশ দেরিতে । গল্প আশির দশকে আর উপন্যাস নব্বুই দশকে । আমার প্রথম উপন্যাস ‘ডুবজলে যেটুকু প্রশ্বাস’ । তবে আমি সব জনারের উপন্যাস লিখেছি, এমনকী ডিটেকটিভ আর ইরটিক উপন্যাসও ।
গোবিন্দ :এ যাবৎ পেয়েছেন অনেক সম্মান।লিখেছেন অনেক গল্প।প্রকৃতপক্ষে বাংলা সাহিত্যের অবস্থান কোন জায়গায়?
মলয় : সম্মান আবার কোথায় পেলুম ? কেবল তো জুতো-লাথি খেয়েছি । বাংলা সাহিত্যের অবস্হান খুবই উঁচু জায়গায় । দুর্ভাগ্যবশত অনুবাদকের অভাব । রবীন্দ্রনাথকেও নিজে অনুবাদ করে ইউরোপীয়দের পড়াতে হয়েছিল ।
গোবিন্দ :প্রেম নিয়ে আপনার ভাবনা?
মলয় : যা জয়দেব, বিদ্যাপতি, ভারতচন্দ্রের, বোদলেয়ারের ।
গোবিন্দ :আপনার প্রেমিকাদেরকে অনেক কবিতা আছে।বলুন।
মলয় : হ্যাঁ । কীই বা বলব । সবই তো রোমিও বলে দিয়েছিল জুলিয়েটকে আর বোদলেয়ার বলেছিলেন জাঁ দুভাল, মাদাম সাবাতিয়ে, মাদাম দোব্রুঁকে ।
গোবিন্দ :কী লিখি কেন লিখি?
মলয় : যা ইচ্ছা হয় লিখি । কী, কেন ইত্যাদি ভাবি না । তবে কী পড়ি আর কেন পড়ি তা বলা যায়।
গোবিন্দ : হাংরি আন্দোলন কি সে অর্থে সফল বলে সমীর রায়চৌধুরী কিংবা আপনিও মনে করেন?
মলয় : এসব তোমরা ভাববে ।
গোবিন্দ ::এই সময় দাঁড়িয়ে কি মনে হয় হাংরি আন্দোলনের প্রয়োজন ছিলো?
মলয় : ছিল নিশ্চয়ই, তা নয়তো হলো কেন ?
গোবিন্দ :কবিতায় শ্লীল অশ্লীল শব্দোচ্চারণের সুস্পষ্ট কোন নিধি নিষেধ হয়?
মলয় : ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রে শ্লীল-অশ্লীলের উল্লেখ বা বর্গীকরণ নেই । ওটা ইসলাম আর প্রোটেস্ট্যান্ট ভিকটোরিয় খ্রিস্টধর্মীদের আমদানি । মনে হয় তা থেকে আমরা শামুকের গতিতে মুক্ত করতে পারছি আমাদের কাজগুলোকে ।
গোবিন্দ :হাংরি আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে কবিতার বাঁক বিশ্লেষণ করেন প্লীজ?
মলয় : আমার যে সাক্ষাৎকারের বই বেরিয়েছে প্রতিভাস থেকে, তাতে পাবে । তালিকাটা দীর্ঘ।
গোবিন্দ :হাংরি আন্দোলনে কারা যুক্ত হয়েছিলেন?এখনো কি তাদের উচ্চারণে হাংরি আন্দোলনের ছাপ আছে?
মলয় : অনেকে । অনেকে । তিরিশ-চল্লিশজন । এখনও লেখায় টিকে আছি আমি । আর যে দুয়েকজন বেঁচে আছেন, তাঁরা লেখালিখি ছেড়ে দিয়েছেন বা স্বাস্হের কারণে লিখতে পারেন
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
-
গুরুচণ্ডা৯-র গ্রাহক হোন
কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে গুরুচণ্ডা৯-র গ্রাহক হোন। গুরুচণ্ডা৯তে প্রকাশিত লেখাগুলি পেতে চাইলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যুক্ত হোন, অথবা, আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলটির গ্রাহক হোন।
- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই
- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... )
(লিখছেন... অরিন)
(লিখছেন... kk, রমিত চট্টোপাধ্যায়, বিপ্লব রহমান)
(লিখছেন... Aranya )
(লিখছেন... পাপাঙ্গুল)
- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন
(লিখছেন... সৃষ্টিছাড়া, সমরেশ মুখার্জী)
(লিখছেন... Prabhas Sen, Ranjan Roy, পড়ুন)
(লিখছেন... সমরেশ মুখার্জী, Kishore Ghosal, সমরেশ মুখার্জী)
(লিখছেন... Muhammad Sadequzzaman Sharif, Muhammad Sadequzzaman Sharif, দীপ)
(লিখছেন... dc, পলিটিশিয়ান, dc)
- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... পাপাঙ্গুল)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... jsl)
(লিখছেন... অরিন, &/, অরিন)
(লিখছেন... lcm, পাঠক, সুকি)
- কি, কেন, ইত্যাদি
- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...
- আমাদের কথা
- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...
- বুলবুলভাজা
- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...
- হরিদাস পালেরা
- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...
- টইপত্তর
- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...
- ভাটিয়া৯
- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...
- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।