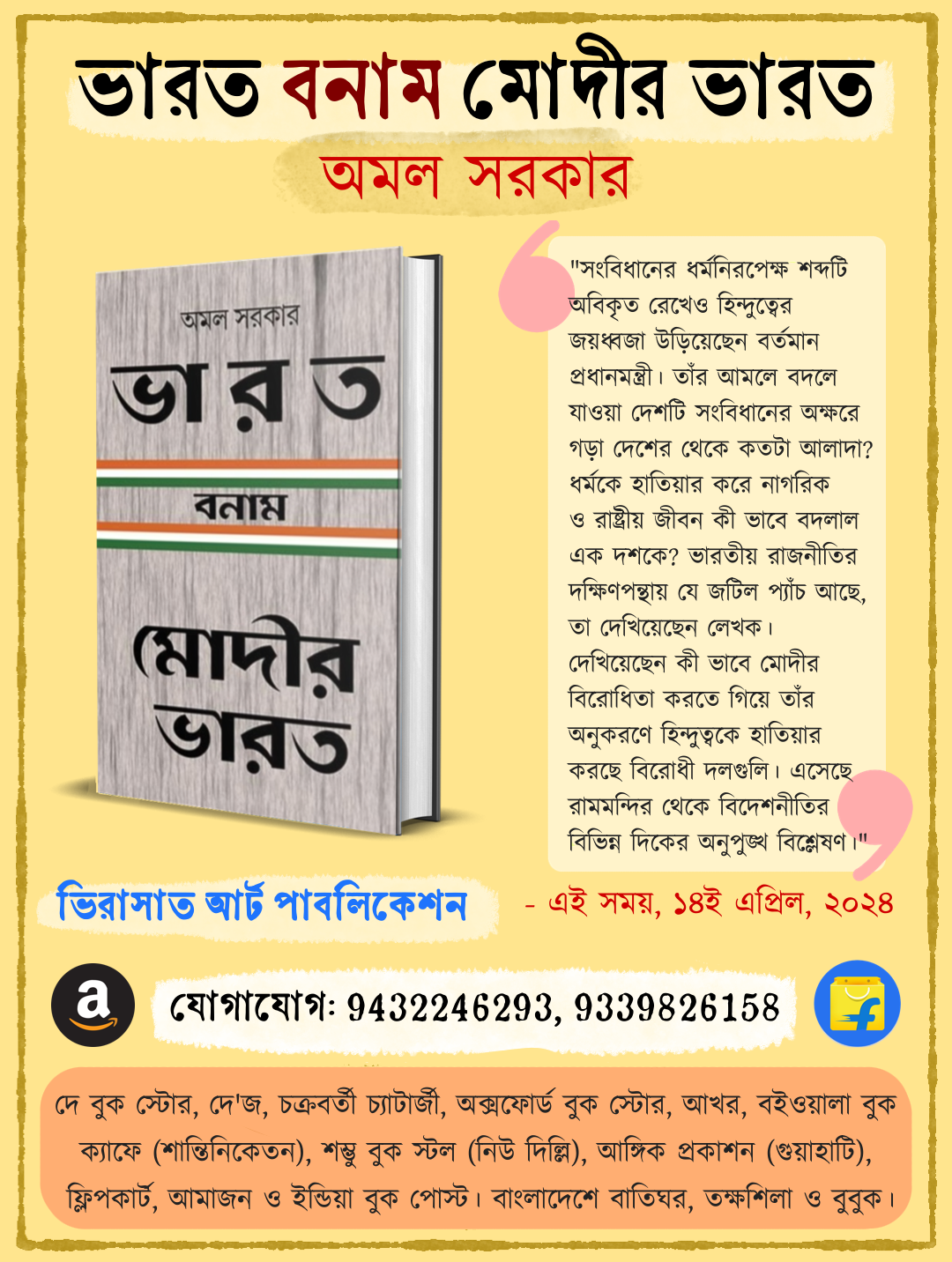মলয় রায়চৌধুরীর কবিতা
বাংলা সাহিত্য নিয়ে যাঁরা ভাবাভাবি করেন, তাঁদের কিছু মজার প্রবণতা আছে। তাঁরা কবিতাকে গদ্য থেকে একেবারে আলাদা করে দেখেন, ও সেই দেখা চিরস্হায়ি করতে নানাবিধ সাংস্কৃতিক প্রপেরও আয়োজন রয়েছে। যেমন রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বেশিরভাগ অনুষ্ঠানেরই নাম--- কবিপ্রণাম । রবীন্দ্রনাথকে মূলত দেখা হয় কবি হিসাবে। গল্পকার, প্রাবন্ধিক, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, সঙ্গীতজ্ঞ রবীন্দ্রনাথ তেমন গুরুত্বপূর্ণ লোক নন। আমাকে প্রশ্ন করলে আমি বলব, গল্পলেখক রবীন্দ্রনাথই আমার কাছে সর্বাধিক গ্রাহ্য । যদিও রবীন্দ্রনাথের গল্প লেখার দর্শন আমার কাছে একেবারেই গ্রহণীয় নয়, তবু 'কবি' রবীন্দ্রনাথের চেয়ে, এই লোকটি আমার চোখে ঢের বাস্তব।
কবিতাকে আলাদা করে দেখা, তাকে সুউচ্চ বেদিতে বসিয়ে রাখা, অহরহ গুজগুজ-ফিসফিস, আরে আজও যাচ্ছেতাই কাণ্ড ঘটিয়ে চলেছে বাংলা সাহিত্যে ও মধ্যবিত্ত জনজীবনে । এ নিয়ে চিন্তা করেছি, আজও মাঝে-মাঝে করি। এ ভাবনার উৎস কোথায়?কিছুটা কি "ভারতীয় অতীত"- এর ব্যাপার রয়েছে এর মধ্যে। বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত--- সবই কবিতায় । কবিকে রহস্যময় মানুষ মনে করা হত, যিনি নিজের চিন্তা-ভাবনাকে ছন্দবদ্ধ করতে সক্ষম। মনে করা হত স্বয়ং ঈশ্বর তাঁর কাছে বার্তা পাঠিয়ে থাকেন। ভগবানের স্পেশাল মেসেঞ্জার তিনি, 'নট টু বি টেকন লাইটলি'। তার বহু পরে, 'ভক্তি' যুগে ভারতীয় সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য কয়েকজন কবিকে সাধক বানিয়ে কুলুঙ্গিতে লাল শালু মুড়ে রেখে দেওয়া হল।কবীর, দাদু, নানক, সুরদাস, রহিম, জয়দেব, চণ্ডীদাস । তুলসীদাসকে 'গোঁসাই' বানিয়ে তাঁরও একই হাল করা হল।'রামচরিতমানস'কে ধর্মগ্রন্হ মনে করে গদগদ আপামর হিন্দিভাষী জনসাধারণ। তার দোহায় দোহায় শব্দের যে অদ্ভুত খেলা, ভাষাকে কাদার মতো ব্যবহার করে তা থেকে বিচিত্র নানা মূর্তি গড়ে তোলা, সেদিকে দুচারজন ক্রিটিক ছাড়া কারো নজরই যায়নি প্রায়। হিন্দি সাহিত্য ঐশ্বরিক বিশ্বাস থেকে মুক্ত হয়ে কবে একাজে হাত দেবে জানি না । আজকে ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে মনে হয়, এ-কাজ করার সময় এসে গেছে ।
ইংরাজপূর্ব বাংলার গ্রামাঞ্চল কিন্তু কবিকে অনেক সহজভাবে নিয়েছিল। কথক ও কবিয়াল ছিলেন, কবিগান ছিল। যাত্রার, পালার আসর ছিল, চণ্ডীতলা ছিল। অবশ্যই কবিকে স্পেশাল টেকনিকে দক্ষ লোক মনে করা হত; তবে সাউক বা অবতার, বা ভগবান নয় । কবির লড়াইতে তো কবিতা তৈরি হত সর্বসমক্ষে, মুখে-মুখে। আর হারজিতও ছিল। কাজেই রহস্যের সেখানে কোনো ভূমিকাই ছিল না । কবি স্পেশাল টেকনিকে দক্ষ বলে তাঁদের আদর-আপ্যায়নও হত, তবে তাঁকে একটি বেদিতে বসিয়ে তাঁর মুখের ওপর স্পটলাইট জ্বেলে রাখা ? নাঃ ! ইংরাজপূর্ব বাংলার গ্রামাঞ্চলে তা করা হত না।
ইংরাজরা আসার পর বাংলা সাহিত্যে কবিতার রহস্যের আমদানি হয় । নিজস্ব সংস্কৃতি বলতে ইংরাজদের কিছু ছিল না। যাকে তারা নিজের সংস্কৃতি বলত, তার খুঁটিগুলো সবই ছিল গ্রিস, রোম থেকে ধার করা। গ্রিসে 'বার্ড' বা ভ্রাম্যমান কবিদের নিয়ে রহস্য গড়ার অভ্যাস প্রচলিত ছিল। ভক্তি যুগের আদলেই প্রায় বলা যায়, তাঁদের 'ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা', ঐশ্বরিক ক্ষমতার অধিকারী, ইত্যাদি মনে করা হত। হোমারের স্হান গ্রিক মানসে প্রায় ঋষির জায়গাতেই ছিল, দাড়ি-টাড়ি সমেত। শেকসপিয়রও আরও কয়েকশো বছর আগে জন্মালে ঐ জায়গাতেই পৌঁছে যেতেন। আমাদের সৌভাগ্য, তিনি পরে জন্মানোর দরুন বিশ্বসাহিত্য একটি নিদারুণ দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে গিয়েছিল।
রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং, সাহিত্যিক জীবনের পরবর্তীপর্বে, কবিতার বিশেষত্বের জায়গা থেকে অনেকটা সরে এসেছিলেন। যাকে সাহিত্যের বিশেষজ্ঞরা 'গদ্য কবিতা' বলেন, তা তাঁর এই বোধের সাক্ষ্য দেয়। তাঁর কিছু গদ্য কবিতা গল্পকেন্দ্রিক। সাহিত্যকর্ম ইশাবে অনেক উঁচু দরের কাজ সেগুলো। মোদ্দা ব্যাপার হল, আজ পাড়াব-পাড়ায় 'কবি প্রণাম' সত্ত্বেও সাহিত্যের বিভিন্ন ফ্যাকাল্টির মাঝখানের দেওয়াল ধ্বসিয়ে দেবার পক্ষপাতী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। তাঁকে বাঙালি এত বেশি 'কবি' বানিয়ে ফেলেছিল যে হাত খুলে এই কাজটি করা সম্ভব ছিল না তাঁর পক্ষে। তবে কাজের মধ্য দিয়ে ঠারে-ঠারে যতটা পেরেছেন, করেছেন। বিশেষ করে ছবি আঁকার মাধ্যমে।
কবিতাকে বা কবিকর্মকে ঘিরে একটা রহস্য সৃষ্টি করে রাখলে কবিতা কখনই সামাজিক পরিস্হিতির দলিল হয়ে উঠতে পারে না। কবিতার মিস্টিসিজমের প্রথম অসুবিধে এটা। কবিতা যদি সামাজিক পরিস্হিতির দলিল না হয়, তবে তাকে ড্রইংরুম সাজানোর ডলপুতুল বা অশ্রুমোছার রুমাল হয়ে থাকতে হয় কেবল।সেটা অবশ্য অনেকেরই মনঃপূত, বিশেষ করে যাঁরা 'সমাজ-টমাজ'কে দশ হাত দূরে রাখতে চান। সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো সাহিত্যেও লড়াই আছে, পক্ষ-প্রতিপক্ষ আছে। একটি পক্ষের বিশেষ দর্শন এটাই। কবিতার গায়ে গরম হাওয়ার ঝাপটা যেন না লাগে।
কবিতার মিস্টিসিজমের দ্বিতীয় অসুবিধে ভাষার স্তরে। ভাষা তো একটি নদী বিশেষ। একূল-ওকূল দুকূলই সে ভাসায়। তাকে সিমিলি, মেটাফর, ছন্দবৃত্ত, মাত্রা, পয়ার ইত্যাদির গণ্ডীর মধ্যে সর্বদা বেঁধে রাখা যায় না। কবিতার নিয়মানুবর্তিতা থেকেই কবিতার মিস্টিসিজমের জন্ম। এই নিয়মানুবর্তিতার দরুনই, একটি বিশেষ শ্রেণীর প্রয়োজন অনুভূত হয়, যে কবিতা 'লিখতে পারে'। যে 'পারে না', তাকে দূর করো, দাঁড় করিয়ে রাখো দরজার বাইরে। তার ভাষাটিও ব্রাত্য।
তাই, কবিতার স্বার্থেই, কবিতার রহস্যময়তাকে ভাঙা অত্যন্ত প্রয়োজন।
বাংলা সাহিত্যের সিরিয়াস পাঠক সম্প্রতি নড়ে-চড়ে বসেছেন। ষাটের দশকে, যে একটি তুমুল ওলোট-পালোট ঘটে গিয়েছিল বাংলা সাহিত্যে, বিশেষ করে বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে--- সেদিকে নজর গেছে তাঁদের। দেরিতে হলেও, এটাই কাম্য ছিল।'হাংরি আন্দোলন' নিয়ে ইতিপূর্বে 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' গোছের কথাবার্তা হয়েছে। 'হাংরি আন্দোলনকারীদের' গভীর মননশীল পঠন-পাঠন ছিল, যাকে বলা যায় ওভারভিউ। হাংরির পরেও আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন এসেছে, তবে সামাজিক-সাংস্কৃতিক ঝাঁকুনি হিসাবে হাংরিই ছিল "প্রথম"। বাংলা সাহিত্যের অবস্হা, হাংরি আন্দোলনের আগে ছিল অকালবৃদ্ধ আফিংখোরের মতো। রবীন্দ্র ঐতিহ্য পুঁটুলি বেঁধে কোলে নিয়ে বসে ঝিমোনো আর মাঝে-মাঝে চটকা ভেঙে, "অ্যাই, গোল কোরো না বলচি, পড়াশুনো করো, পড়াশুনো..."। অথচ দেশে-বিদেশে তখন ঘটছে যুগান্তকারী ঘটনা । 'গ্রানমা' জাহাজে চড়ে বিপ্লব করতে আসা কয়েকজন যুবক হঠাৎ জয়ী হয়েছেন। ওয়াশিংটন থেকে মাত্র নব্বই মাইল দূরে দেখা দিয়েছে বিদ্রোহের পতাকা। ওদিকে ঠাসবুনোট সমাজতান্ত্রিক মূল্যবোধ ক্রমে ঠোঙা বানাবার কাগজ বই আর কিছু নয়। স্হিতাবস্হাকামী বাণিজ্যিক সংবাদপত্র গোষ্ঠীর প্রচণ্ড একমাত্রিক দাপট বাংলা সাহিত্যে। তার দোরগোড়ায় মাথা না ঠুকলে কেউ মানুষই হবে না, সাহিত্যিক হওয়া তো দূরে রইল।
এইরকম সময়ে বাংলা সাহিত্যের 'পীঠস্হান' কলকাতা থেকে দূরে, পাটনা শহরে, যেখানে ঐশ্লামিক ধর্মশাস্ত্র পড়তে গিয়েছিলেন রামমোহন রায়, আর বেশ কয়েক বছর চাকরি করে গেছেন দীনবন্ধু মিত্র, সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে একটি অপরিচিত গরিব পরিবারের যুবক মলয় রায়চৌধুরী আই আন্দোলনটির ছক কষেন। দাদা সমীর রায়চৌধুরী কলকাতায় সিটি কলেজে পড়েন, সেই সুবাদে যুবা বাঙালি লেখক-কবিদের সাথে আলাপ-পরিচয় । দেশ-দুনিয়ে জুড়ে উথালপাথাল সত্ত্বেও কলকাতা, ব্রিটিশের প্রিয় 'কালকুত্তা' তখনও শীতল। বামপন্হী দলগুলোর বিরুদ্ধে গান্ধীবাবার কংগ্রেস প্রতিপালিত গোপাল পাঁঠা, ইনু মিত্তিরদের দাপাদাপি; কলকাতা শীতল। কবিতা ভবন (!) থেকে 'কবিতা' বেরোয় । বুদ্ধদেব বসুর পরিশীলিত আঙুল কবি বাছাই করে, ফতোয়া দেয়। দোর্দণ্ডপ্রতাপ সেই উপস্হিতি। এককালে...'না না অমন বলবেন না । সুকান্তও কবি। ছন্দ বোঝে। এই দেখুন আমি দেখাচ্ছি --- পতা/কায় পতা/কায় ফেরমিল/আনবে ফেব্রু/য়ারি। দেখলেন ?
অট্টহাসি উদ্রেক করা সেই সময়। সমীর রায়চৌধুরীর 'পাটনাই' হওয়ার দরুন কলকাতার যুবক কবিদের পাটনায় আনাগোনা। এঁদের মধ্যে অন্যতম শক্তি চট্টোপাধ্যায়। যাঁর বিষয়ে বাসব দাশগুপ্তকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মলয় বলেছেন, "শক্তির কবিতা সম্পূর্ণ নিজস্ব ও অসাধারণ। কেননা তিনি পাঁড় অশিক্ষিত, কোনো লেখাপড়া করেন না, এবং দর্শন, ইতিহাস, সমাজবোধ এসব ছিটেফোঁটা তাঁর মধ্যে নেই। নিজের খাঁটি বোধ থেকে তিনি লেখেন, তখন তাঁকে জীবনানন্দের পরের প্রভূত ক্ষমতাসম্পন্ন মনে হয়।" মনে রাখা প্রয়োজন, এই সাক্ষাৎকারটি যখন দিচ্ছেন মলয়, তখনও হাংরি আন্দোলনের স্মৃতি, তজ্জনিত তিক্ততা, সব কিছু মলয়ের মস্তিষ্ককোষে উপস্হিত। কিছুই ক্ষমা করেননি। অথচ কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে মলয়ের চোখা, টান-টান মূল্যায়ন। ব্যক্তিগত তিক্ততা সেখানে ছায়া ফেলেনি।
হাংরি আন্দোলনের পরিকল্পনাপর্বে এই শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে মলয় সঙ্গে পেয়েছিলেন, আর পেয়েছিলেন দেবী রায় ( হারাধন ধাড়া) কে। পাটনার সুবিমল বসাক এসে যোগ দেন কিছুকাল পরে।একটি সাহিত্য আন্দোলন, যা বাংলা সাহিত্যের হাল-হকিকত পালটে দিয়েছিল, কত সামান্যভাবে শুরু হয়েছিল, ভাবলে অবাক লাগে। প্রেস পাওয়া যাচ্ছিল না, তাই মিষ্টির দোকানের বাকসো যে জব প্রেস ছাপতো, সেখানেই ছাপতে হয় হাংরি বুলেটিন। রিজার্ভ ব্যাঙ্কে মলয় তখন লোয়ার গ্রেড কেরানির চাকরিতে, কত মাইনে পেতেন জানা নেই, তবে প্রায় সম্পূণফ মাইনেটাই মনে হয় হাংরি বুলেটিনের পেছনে ঢালতে হত। বাংলা সাহিত্যে, বিশেষ করে বাংলা কবিতায়, পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রথম কাগজ বেরোনোর আরম্ভটা এইরকম। 'শতভিষা' পত্রিকার তুলনায় 'কৃত্তিবাস' ও নিজেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাগজই বলত, তবে হাংরি বুলেটিনের সাথে তার ছিল মৌলিক প্রভেদ। 'কৃত্তিবাস' ছিল সাহিত্যিক উচ্চাকাঙ্খীদের কাগজ। তাঁদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছিল প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংঘর্ষ এড়িয়ে সুরে সুর মিলিয়ে। প্রতিষ্ঠান কখন যশ, প্রতিপত্তি, বৈভব, টাকাকড়ি, সামাজিক সুবিধার কাজে লেগে যায়, বলা তো যায় না। হাংরি বুলেটিনের উদ্দেশ্যই ছিল যুদ্ধ। আপসের জন্যে সেখানে কোনও জায়গাজমি রাখা হয়নি।
অনেকের মতে হাংরি আন্দোলনকারীরা কয়েকটি গিমিকের আশ্রয় নিয়েছিলেন রাতারাতি খ্যাত হবার জন্য, যেমন শাদা দিস্তা কাকজ, জুতোর বাকসো ইত্যাদি রিভিউএর জন্য পাঠানো, টপলেস প্রদর্শনীর আয়োজন ( টপলেসের অর্থ যে মুন্ড বা মস্তিষ্কবিহীনও হয়, এই বোধটুকু কলকাতার বুদ্ধিজীবীদের হয়নি), জীবজন্তু-জোকারের মুখোশ বিলি ইত্যাদি। 'হাংরি কিংবদন্তি'তে মলয় উদ্ধৃত করেছেন আবু সয়ীদ আইয়ুবের যে মন্তব্য, তা এ-প্রসঙ্গে দেখা যেতে পারে।কিন্তু মলয় বা তাঁর সঙ্গীরা কি জানতেন না যে প্রতিষ্ঠান ও প্রসাশন কতদূর হিংস্র হতে পারে? এ জানা সত্ত্বেও একজন চাকুরিজীবী ( মলয় ) নিজেকে এই ঝুঁকির সামনে এগিয়ে দিয়েছিলেন কেন ? শুধুই প্রচারের জন্য? না কি কিছু মূল্যবোধের ব্যাপারও ছিল ? মলয় তাঁর 'সাক্ষাৎকারমালা'র এক জায়গায় বলেছেন, 'ষাট দশকের সুস্হতা স্বাভাবিক ছিল না।' এই অস্বাভাবিক সুস্হতাকে ভালোমতো একটা ঝাঁকুনি দেওয়াই উদ্দেশ্য ছিল তাঁর। তার জন্য দুহাতে হাতকড়া, কোমরে দড়ি পরে চোর-ডাকাতের সঙ্গে সার বেঁধে পাটনা শহরের রাস্তায় অতিপরিচিতজনের মাঝে হাঁটা, চাকুরি থেকে সাসপেন্ড হওয়া, পঁয়ত্রিশ মাস প্রতি সপ্তাহে কাঠগড়ায় দাঁড়ানো--- সবই। প্রচার পাওয়ার জন্য যদি এত করতে হয়, তাহলে তো মুশকিল। এর চেয়ে সহজ রাস্তা তো কতই ছিল। বিশেষত, 'কৃত্তিবাস' গোষ্ঠীতে তাঁর দাদার বন্ধুরাই যখন সর্বেসর্বা। সমসাময়িক অন্যান্যদের মতন একটু মিঠে ব্যবহার রাখলেই আর দেখতে হচ্ছিল না। আর, 'কৃত্তিবাস'ও তেমন-তেন বৈশিষ্টহীন ও লুপ্ত হবার পথে এগিয়েছে। সাহিত্য আন্দোলন সম্পর্কে 'কৃত্তিবাসীয়'দের সততার এর চেয়ে ভালো উদাহরণ আর কী হতে পারে ?
( দ্রষ্টব্য: কবিতীর্থ, মাঘ ১৪১০)
বলা যেতে পারে যে 'কৃত্তিবাস' যদি সাহিত্য পত্রিকা হিসেবে না টিকে থাকে তবে 'হাংরি বুলেটিন'ও তো টেকেনি। হ্যাঁ, হাংরি বুলেটিন উঠে গিয়েছিল মামলা-মকদ্দমার দরুন, অন্তর্কলহের দরুন। কিন্তু হাংরিদের ঝগড়াঝাঁটি ছিল খোলাখুলি, তাতে মধ্যবিত্তের চাপ-চাপ ঢাক-ঢাক ছিল না। মামলা-মকদ্দমার ভয়ে কেউ রাজসাক্ষী হয়েছিলেন ( সুভাষ ঘোষ,শৈলেশ্বর ঘোষ, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, উৎপলকুমার বসু প্রমুখ ), কেউ ভেবড়ে গিয়ে কলকাতার বাইরে কেটে পড়েছিলেন ( প্রদীপ চৌধুরী, সুবো আচার্য প্রমুখ )। সেগুলোকে দেখার কোনও অর্থ হয় না।'হাংরি বুলেটিন' বন্ধ হবার পর অগনণ পেশিবহুল বাহু এগিয়ে এসেছে আন্দোলনের পতাকা তুলে নিতে।জেব্রা, উন্মার্গ, ফুঃ, স্বকাল, ক্ষুধার্ত খবর, জিরাফ, কনসেনট্রেশান ক্যাম্প, ওয়েস্ট পেপার, চিহ্ণ, প্রতিদ্বন্দী ইত্যাদি পত্রিকাও হাংরি বুলেটিনই। মলয় কোনোদিন বলেননি যে হাংরি আন্দোলনের কপিরাইট একমাত্র তাঁর। হ্যাঁ, আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ও দার্শনিক প্রতিনিধি হিসাবে তাঁর কিছু বক্তব্য থাকতেই পারে, যা তিনি বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে পাঠকদের সামনে রেখেছেন।এই অধিকার থেকে তো আর তাঁকে বঞ্চিত করা যায় না। মলয়ের পরবর্তীকালীনরা হাংরি মতাদর্শকে নিজেদের মতো করে ব্যাখ্যা করেছেন।এটিও একটি আন্দোলনের প্রাণশক্তির প্রমাণ। মলয়, হাংরি আন্দোলন ফুরিয়ে যাবার পর, পড়ালেখার নিজস্ব পৃথিবী গড়ে তুলেছেন, মন দিয়ে এবং চুটিয়ে বিভিন্ন শহরে চাকরি করেছেন, সংসার করেছেন, ভারতীয় জনজীবনকে দেখেছেন, জীবন থেকে শিখেছেন। আজ গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক, প্রবন্ধের যে হতচকিত-করা ফসল তিনি আমাদের হাতে তুলে দিচ্ছেন তা সম্ভব হতে পেরেছে এরই দরুন। বাণিজ্যিক সাহিত্য প্রতিষ্ঠানের গদি-আঁটা চেয়ারে বসে আঙুলে চাবির রিং ঘোরাননি মলয়। এর জন্য তাঁর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। অন্তত একটি আকাশ এমন রয়েছে, যাকে ঢেকে ফেলতে পারেনি কালো মেঘ।
মলয়কে 'প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার' কবিতাটির দরুন মামলায় পড়তে হয়। কবিতাটি বর্তমানে বহুল প্রচারিত, তাই তাকে আর সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করার প্রয়োজন নেই। তবে এই কবিতাটিকে কেন্দ্র করে অশ্লীলতা ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র মামলা, যদি ধরেও নেওয়া যায় যে এর পেছনে কোনো অসূয়া কাজ করছিল না, একটি কৌতুকপ্রদ মাইন্ডসেট-এর দিকে ইঙ্গিত করে। এই মাইন্ডসেটটি তদানীন্তন বুদ্ধিজীবী বাঙালির, যিনি পুজোর ছুটিতে সস্ত্রীক খাজোরাহো দেখতে যান। তাহলে মলয়ের কবিতা কেন গ্রহণীয় নয় ? মজা কেবল এই জায়গাটুকুতে নয়, অন্যত্রও আছে। "আমরা যখন অসভ্য ছিলুম তখন ওইগুলো বানিয়েছি। এখন আমরা সভ্য, এখন তো আর এসব চলতে দেওয়া যায় না ।" এও মানলাম, কিন্তু মাই ডিয়ার, ব্যাপারটা যে আদপে তা নয় একেবারেই। ব্যাপার আগাগোড়া অন্যরকম। যৌন রূপকল্প, দ্যোতক ও বিম্ব কেবল ব্যবহার করেছেন মলয়, সেগুলির মাধ্যমে নিজের কথা বলেছেন। এও চলবে না ? তাহলে শিবলিঙ্গ তুলে দিন, গৌরীপট্ট নাকচ করুন, অম্বুবাচী ব্যান করুন। কামাখ্যা মন্দিরে মা-কামাখ্যার মাসিক যেন আর না হয়। কি বলেন ? যাঁরা "অশ্লীল অশ্লীল" চিল্লিয়েছিলেন, তাঁরা সম্ভবত 'প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার-এর এই লাইনগুলো নজর করে দেখেননি--
১.
জন্মমুহূর্তের তীব্রচ্ছটা সূর্যজখম মনে পড়ছে
আমি আমার নিজের মৃত্যু দেখে যেতে চাই
মলয় রায়চৌধুরীর প্রয়োজন পৃথিবীর ছিল না
তোমার তীব্র রূপালি য়ুটেরাসে কিছুকাল ঘুমোতে দাও শুভা
শান্তি দাও, শুভা শান্তি দাও
২.
হুঁশাহুঁশহীন গাফিলতির বর্ত্মে স্ফীত হয়ে উঠছে নির্বোধ আত্মীয়তা
আ আ আ আ আ আ আ আ আঃ
মরে যাব কিনা বুঝতে পার্ছি না
তুলকালাম হয়ে যাচ্ছে বুকের ভেতরকার সমগ্র অসহ্যতায়
সবকিছু ভেঙে তছনছ করে দিয়ে যাব
শিল্পর জন্যে সক্কোলকে ভেঙে খান-খান করে দোবো
কবিতার জন্যে আত্মহত্যা ছাড়া স্বাভাবিকতা নেই...
৩.
এরকম অসহায় চেহারা ফুটিয়েও নারী বিশ্বাসঘাতিনী হয়
আজ মনে হয় নারী ও শিল্পের মতো বিশ্বাসঘাতিনী কিছু নেই
এখন আমার হিংস্র হৃৎপিণ্ড অসম্ভব মৃত্যুর দিকে যাচ্ছে
মাটি ফুঁড়ে জলের ঘূর্ণি আমার গলা ওব্দি উঠে আসছে
আমি মরে যাব...
৪.
৩০০০০০ লক্ষ শিশি উড়ে যাচ্ছে শুভার স্তনমণ্ডলীর দিকে
ঝাঁকেঝাঁকে ছুঁচ ছুটে যাচ্ছে রক্ত থেকে কবিতায়
এখন আমার জেদি ঠ্যাঙের চোরাচালান সেঁদোতে চাইছে
হিপ্নটিক শব্দরাজ্য থেকে ফাঁসানো মৃত্যুভেদী যৌনপর্চুলায়
ঘরের প্রত্যেকটা দেয়ালে মার্মুখী আয়না লাগিয়ে আমি দেখছি
কয়েকটা ন্যাংটো মলয়কে ছেড়ে দিয়ে তার অপ্রতিষ্ঠিত খেয়োখেয়ি
এই পঙক্তিগুলো একটু মন দিয়ে পড়লে বাঙালি মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর পক্ষে বোঝা দুষ্কর ছিল না যে নিছক যৌনতা নয়, আরো গূঢ় কোনো বোধের দ্যোতনা এই পঙক্তিগুলোয় রয়েছে।'সাত বছর আগের একদিন' কবিতায় জীবনানন্দ লিখেছিলেন, "অর্থ নয় কীর্তি নয় স্বচ্ছলতা নয় আরও এক বিপন্ন বিস্ময় আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে খেলা করে। আমাদের ক্লান্ত করে, ক্লান্ত ক্লান্ত করে। লাশকাটা ঘরে সেই ক্লান্তি নাই..."। এই পঙক্তিগুলোকে উদ্ধৃত করে জীবনানন্দকে শবসাধক সাব্যস্ত করা অবশ্যই উচিত হবে না, অথবা ঘোর অঘোরপন্হী। তেমনই হাস্যকর 'প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার'-এ যৌনতার বহিঃপ্রকাশ খোঁজা। আসলে মলয়ের বিরুদ্ধে যখন ষাটের দশকে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও অশ্লীলতার মকদ্দমা দায়ের করা হয়, তখন ষাটের দশকের 'অস্বাভাবিক সুস্হতা' রাজত্ব করছে পুরোদমে।'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হচ্ছে প্রবোধকুমার সান্যালের 'দেবতাত্মা হিমালয়' আর মেট্রো সিনেমার ফুটে রিফিউজি যুবতীদের শরীর নিয়ে চলছে অবাধ বাণিজ্য! পায়ের চটি ঘষটাচ্ছে রিফিউজি যুবক, 'মাই ওন সিসটার স্যার, ভেরি সুইট, ওনলি সিক্সটিন'। অথচ বাঙালি পাঠক 'কত অজানারে'র বারবেল সাহেব আর 'সখী সংবাদ' এর মিষ্টিদিদি, নতুন দিদি, এদের নিয়েই মুগ্ধ। সমাজ কোথাও নেই; সমাজের জ্ধবলাপোড়া, আর্তি, চিৎকার এগুলোও কোথাও নেই। বামপন্হীরা 'পরিচয়' পত্রিকা চালাচ্ছেন, তাতেও এন্ট্রি পারমিট নিয়ে ঢুকতে হয়। এইরকম এক সময়ে 'হাংরি বুলেটিন' এর দরকার ছিল, প্রয়োজন ছিল 'প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার'-এর। মূল্যবোধ ভেঙে খানখান হওয়ার যে হরর, শিল্পপ্রতীক জোলো হয়ে যাওয়ার যে শক, তাকে যথার্থ ফুটিয়ে তুতে গেলে এই কবিতাই তো লিখতে হবে। মলয় তাই করেছিলেন।
অবশ্য বিপদ চেনার ব্যাপারে প্রশাসন ও প্রতিষ্ঠানের সূক্ষ্মদৃষ্টির প্রশংসা করতেই হয়। কেই বা পড়ে তখন 'হাংরি বুলেটিন', কটা লোক ? পাটনার দুই যুবক, একজন হাওড়ার, একজন বিষ্ণুপুরের, একজন শান্তিনিকেতনের, এদের বুলেটিন বেরোয়। তার জন্যও আবার এই প্রেস, ওই প্রেসের হাতে-পায়ে ধরাধরি। তাহলে? এমন কী ক্ষমতাসম্পন্ন এরা, যে ক্ষেপে উঠল গোটা কলকাতার বাণিজ্যিক সাহিত্য প্রতিষ্ঠান ও সরকারি প্রশাসন ? মলয়ের বিরুদ্ধে কেবল মামলাই নয়, তাঁকে ও অন্যান্য হাংরি আন্দোলনকারীদের গ্রেপ্তার করে অপমান করা হল চরম, যাতে ভবিষ্যতে আর কোনোদিন এই জাতীয় প্রবণতা মাথা তোলার হিম্মত না করে ।
বাণিজ্যিক সাহিত্য প্রতিষ্ঠান ও প্রশাসন যে সমাজকে বুঝতেন না তা নয়, ভালোমতোই বুঝতেন। তাঁরাও জানতেন যে, যে-বদমায়েশি তাঁরা শিল্প, সাহিত্য, সমাজ, সংস্কৃতির সর্বত্র বিছিয়ে রেখেছেন, তা মানুষের জন্য নয় । তবে শ্রেণী স্বার্থে এর প্রয়োজন তাঁদের ছিল। যেমন ইংরেজরা, আই.সি.এস.কে লৌহ কাঠামো হিসাবে গড়ে তুলতে ছেয়েছিল, তেমনই উত্তর-স্বাধীনতা যুগের ভারতীয় পুঁজিবাদ, আমলাতন্ত্র ও তার মিডিয়া-খানসামাদের লক্ষ ছিল একটি জড়, নির্বোধ, সংবেদনহীন মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে তোলা। তাদের রুচি, জীবনযাপন, মূল্যবোধ, সব কিছু হবে ছাঁচে ঢালা, সিনথেটিক। তারা হাসবে, কাঁদবে, গাইবে, সঙ্গম করবে একটি বিশিষ্ট কায়দায়। 'হাংরি প্রজন্ম'এর হুড়মুড় করে এসে পড়ায় এই গোটা গেমপ্ল্যানটি ধ্বসে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। মলয় এবং অন্যান্যদের ওপর আক্রমণ সেই কারণেই।
প্রজাপতি-আঁকা বিয়ের কার্ডে হাংরি প্রজন্ম ধ্বনি তুলেছিল, "গাঙশালিক কাব্যস্কুলের জারজদের ধর্ষণ করো"। এই ধ্বনিটিতে অন্তর্নিহিত ছিল তদানীন্তন কাব্যধারার প্রতি বিবমিষা।
প্রকৃতি, নিসর্গ এই ব্যাপারগুলো হয়ে দাঁড়িয়েছিলো বাংলা কবিতার কলোনোয়াল রোগবিশেষ। রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহ ছিল একটা কমপালশান, যেমন লেখালিখি ছিল তাঁর কমপালশান। সেজন্য তাঁর লেখায় প্রকৃতি, নিসর্গ বিশেষভাবে উপস্হিত--- কবিতায়, নাটকে, উপন্যাসে। আঁকার সময়ে তিনি এগুলো বর্জন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। পরে, বাংলা কাব্যধারায় এই ব্যাপারগুলো প্রয়োজনীয় অনুপান হয়ে ওঠে। এবং অনুপানেরও অধিক, অভ্যাস।জীবনানন্দ লেখেন 'রূপসী বাংলা'। তাতেও নিসর্গ ছিল; তবে সেই নিসর্গ, প্রকৃতির প্রতিটি কমপোনেন্ট আবহমানের বাঙালিজাতির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলোর প্রতিনিধিত্ব করেছিল।মানুষের সাথে সম্পর্কবিহীন ছিল না সেই নিসর্গ, সেই প্রকৃতি।সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, "একদা আষাঢ়ে এসেছি এখানে, মিলের ধোঁয়ায় পড়ল মনে; কালবৈশাখী নামবে যে কবে আমাদের হাত-মেলানো গানে"। এখানে মানুষের সংগ্রামকে আঁকা হয়েছে প্রাকৃতিক ঘটনার রং-তুলিতে। কিন্তু বাংলা ভাষার সেইসব কবিরা (গাঙশালিক কাব্যস্কুল) সৃষ্টি করছিলেন মনুষ্যবিহীন নিসর্গ, মানুষকে মাইনাস-করা প্রকৃতি। এ ছিল একজাতীয় পলায়নবাদ। শংকরের 'কত অজানারে' যেমন বাঙালি যুবকের বেকারত্ব থেকে পলায়ন করতে চেয়ে বারবেল সাহেবের মহানতায় বুঁদ হয়ে থাকা, বিমল মিত্রের মিষ্টি দিদি, নতুন বৌদি, ছোট বৌঠান যেমন নারী-পুরুষের স্বাভাবিক যৌনসম্পর্ক ফেস করতে না চাওয়ার যুক্তি, তেমনই 'গাঙশালিক কাব্যস্কুল' ছিল মানুষের দুঃখ, শোক, রোগ, ঘা-পাঁচড়া এগুলোকে দেখতে না চেয়ে স্টুডিওর পর্দায় আঁকা চাঁদ, তারা, নদী, ফুলে বিভোর হয়ে থাকা। ঠিক তখনই মানুষের জীবনধারণ কতদূর দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছিল, তা দেখতে পাওয়া যায় ঋত্বিক ঘটকের ফিলমগুলোতে। সেই দৈন্য, দুর্দশা, দাঁতে দাঁত চেপে লড়াইয়ের প্রতিফলন এই কবিতাগুলোতে কোথাও ছিল না। কেন ? কেননা, তা করার অসুবিধে ছিল। তা করতে গেলে দীর্ঘ একটা লাফ দিতে হত, বিশেষ করে ভাষার ক্ষেত্রে।ঋত্বিক যেমন 'মেঘে ঢাকা তারা' বা 'কোমল গান্ধার' -এ গোটা ইডিয়মটিকেই ভেঙেচুরে ফেলেছিলেন, তেমনই ষাটের দশকের বঙ্গসমাজ ও মানুষেকে তুলে আনতে গেলে বাংলা কবিতার গোটা ইডিয়মটিকেই ভাঙতে হত। খানিকটা শ্রেণী পরিপ্রেক্ষিত আর কিছুটা গাড্ডায় পড়ে যাওয়ার ভয়, উভয়ে মিলে এ-কাজ করতে দেয়নি বাংলা ভাষার কবিদের। অতএব চাঁদ, তারা, নদী, ফুল, মৌমাছি...
আরেকটি প্রশ্নও ছিল। কবি কি কেবল কবিতাই লিখবেন, না সামাজিক ভাষ্যকারও হবেন ? রবীন্দ্রনাথ কেবল কবি নন, সামাজিক ভাষ্যকারও ছিলেন। জীবনানন্দও তাই ( জীবনানন্দকে নিবীঢ়ভাবে পড়লে এই ব্যাপারটি ধরা পড়ে) । কিন্তু উত্তরোত্তর সামাজিক ভাষ্যের ব্যাপারটি বাংলা কবিতা থেকে উঠে যেতে থাকে। "কবিতা কবিতাই। সামাজিক ভাষ্যটাষ্য আবার কী?" এ-জাতীয় একটী প্রবণতা বাংলা কবিতাকে পেয়ে বসতে থাকে। একে ক্রমাগত হাওয়া দিতে থাকে স্বার্থান্ধ বাণিজ্যিক সাহিত্য প্রতিষ্ঠান।
খুব স্বাভাবিকভাবেই নভেম্বর ১৯৬১-এর প্রথম বুলেটিন থেকেই হাংরি প্রজন্ম এই প্রবণতার বিরুদ্ধে ছিল। সেই দিন থেকে আজ অব্দি মলয়, সামাজিক ভাষ্যকারের ভূমিকাটি কোনোদিনই হাতছাড়া করেননি। 'প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার'এ যেমন সামাজিক বিশৃঙ্খলা নিয়ে তাঁর তীব্র বিবমিষা, তামনই আজও। তাঁর হালের একটি কবিতা নেওয়া যেতে পারে, 'যা লাগবে বলবেন' সংকলন থেকে । কবিতাটির নাম 'ক্ষুধার্ত মেয়ে':
আমার আসক্তি নেই কোনো
চলে যা যেখানে যাবি
যার সঙ্গে শুতে চাস যা
আমি একা থাকতে চাই
ক্ষুধার্ত বা পেটুক মহিলা
যে ঘোরে সবার হাতে
খড়কুটোময় সংসারে
তার কোনো প্রয়োজন নেই।'
কবিতাটিতে জড়িয়ে আছে একটা ঈষৎ বোহেমিয়ান বাচনভঙ্গী। পড়লে মনে হবে কেউ একজন লিখছেন তাঁর শয্যাসঙ্গিনীর উদ্দেশ্যে। এটি কিন্তু কবিতার প্রথম স্তর। দ্বিতীয় স্তরে কবিতা ও সমাজ সম্পর্কে মলয়ের দার্শনিক বোধ সন্নিহিত। শয্যাসঙ্গিনী মহিলাটি আসলে কবিতাই। অথচ সবার হাতে ঘোরার প্রবণতা তার, সে হাত স্মাগলারের হোক বা বিপ্লবীর।কবিতার লয়ালটি সন্দিগ্ধ। ওদিকে সংসার অনিত্য, অতএব তার প্রয়োজন কিসের ?
'প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার' কবিতায় যে-কথা বলার জন্য মলয়কে অনেক বেশি জায়গা ব্যবহার করতে হয়েছে, 'যা লাগবে বলবেন' গ্রন্হে সেই কথাই তিনি বলেছেন অনেক সংক্ষিপ্ত পরিসরে। 'হাংরি আন্দোলন' থেকে সরে এসে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ইন্সপেক্টিং অফিসার হিসেবে ভারতের গ্রামে-গঞ্জে শহরে শহরে ঘোরা, তারপর এ.আর.ডি.সি. ও নাবার্ডের গ্রামোন্নয়ন বিশেষজ্ঞের উচ্চপদে। যদিও মলয় তাঁর এই পরিবর্তিত জীবনশৈলী নিয়ে 'হাংরি কিংবদন্তি' গ্রন্হের শেষে মশকরাও করেছেন, "ছাই-এর জায়গায় আসে টুথপেস্ট, কয়লার উনুনের বদলে গ্যাস, সর্ষের তেলের বদলে সূর্যমুখী, শার্ট-প্যান্টের বদলে সাফারি, মাদুরের স্হানে বিছানা, ঢাবার বদলে রেস্তরাঁ, দিশির জায়গায় স্কচ, কলেজস্ট্রিট ও বইপাড়ার বদলে বাংলার গ্রামশহর।" কিন্তু তবু জীবনের এই অধ্যায়টিও যে কবি হিসেবে মলয়কে অনেক বেশি সমৃদ্ধ করেছে, তাতে সন্দেহ নেই।
'প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার'-এ বাঁধন-ছেঁড়া রাগ ছিল মলয়ের কবিতার পরিচিত চিহ্ণ। কিন্তু এই পর্যায়ে এসে জীবনের বহু কিছু দেখে-শুনে মলয়ের কন্ঠস্বর তেতো, অম্লকষায়, আর তার সাথে এসে জুটেছে আয়রনির অধুনান্তিক পরিহাসও। তবু তা মলয়ের কবিতাকে সর্বজনগ্রাহ্যও করে তোলে বটে।'যা লাগবে বলবেন'-এর আরও একটি কবিতাকে নেওয়া যেতে পারে, যেমন 'দ্রোহ':
এ-নৌকো ময়ূরপঙ্খী
তীর্থযাত্রী
ব্যাঁটরা থেকে যাবে হরিদ্বের
এই গাধা যেদিকে দুচোখ যায় যায়
যাযাবর
ঘাট বা আঘাটা যেখানে যেমন বোঝে
ঘুরতে চাই গর্দভের পিঠে
মাথায় কাগুজে টুপি মুখে চুনকালি
পেছনে ভিড়ের হল্লা ।
ব্যাস! কবিতা এইটুকুই। অথচ বাঙালি সমাজের যে একটি বিশেষ প্রবণতা, কবিকে বেদিতে বসিয়ে রাখার, তাকে কত সার্থক ভাবে ভাঙঅ হয়েছে এখানে। পাটনার অন্ত্যজ মহল্লাগুলোতে হোলির দুতিন দিন আগে থেকে চোখে-পড়া একটি সুপরিচিত দৃশ্যকে ব্যবহার করেছেন মলয়, প্রশ্নাতীত দক্ষতাসহ। তার সাথে মিশিয়েছেন তীর্থযাত্রার জন্য বাঙালি হিন্দুর চিরাচরিত আতুরতাটিকে, যাতে পোস্টমডার্ন পরিহাস আরও তীব্র হয় । আর... হাংরি মামলার সময়ে তাঁকে যে-সামাজিক অবমাননা সইতে হয়েছে, তাও উঠে এসেছে। মাত্র কয়েকটি পঙক্তির মধ্যে কত প্রসঙ্গ যে এসেছে, অথচ বলার ভঙ্গিটি এত সহজ যে ভাবাই যায় না ।
এই সংগ্রহের আরেকটি কবিতা 'যে পার্টি চাইছেন সে পার্টিই পাবেন'।
বিশ্বাস এক দুর্ঘটনা
বুকপকেটে শ্রেণী
প্রতিরোধী থাকেন জেলে
কাজু-ফলের ফেনি
বরং ভালো
ভুল অঙ্কের ডানা।
...মোড়ল দলের পাড়ার কেউ বা
আওড়ায় বেঘোরে
ছাদ ঢালায়ের সমরবাদ্য
কর্তাবাবার জানা
মেলাবেন তিনি অন্তরীক্ষে
মোক্ষ একখানা ।
কবিতার শেষ দুটি পঙক্তিতে অমিয় চক্রবর্তীর 'মেলাবেন তিনি মেলাবেন', এই শান্ত, স্হিত, প্রায় ব্রাহ্ম, উত্তর-রাবীন্দ্রিক বিশ্বাসের আদলটি একেবারে বিপরীত অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে পার্টি আমলাতন্ত্রের যে প্রবল দাপত, যার দরুণ তেলে-জলে মিশ খেয়ে একেবারেই একাকার, পুতুল নাচের সুতোর শেষ প্রান্তটি ব্যক্তিবিশেষের হাতে, সেটিতে যেমন-যেমন টান পড়ছে, কাঠের পুতুলগুলো তেমন-তেমনই নাচছে; এই গোটা পরিবেশটি উঠে এসেছে কয়েকটি মাত্র পঙক্তির মাধ্যমে। মলয় বুঝিয়েছেন, যা বোঝাতে গেলে অন্তত কয়েকশো পাতার বই দরকার। আর? বিরোধীপক্ষ বলতে কিছু নেই আর। যারা বিরোধ করছে, তারাও বস্তুত নিজের-নিজের ছাদই ঢালাই করছে। সেই ছাদ ঢালাই-এর বাজনাকে মানুষ মনে করছে সমরবাদ্য।
এত সূক্ষ্ম যাঁর ভাষার পরিমিতিবোধ, তিনি কিন্তু 'চিৎকারসমগ্র' গ্রন্হে এসে আবার অন্যরকম হয়ে যান। দড়ি ঢিলে দেন একটু, যাতে তাঁর সংবাদবাহক ঘুরতে পারে জায়গা-বেজায়গায়। 'ভাঙনের ছায়াগাছ' কবিতাটির অংশ পড়া যেতে পারে এই প্রসঙ্গে:
হাজত থেকে ছাড়ান-পাওয়া সেই প্রৌঢ় নদী
নাচছে দুর্গাবোঙার ফরসা কোমর জড়িয়ে
শহর-পুরুতের গামছা কাঁধে
তাককা হুরে
আরে হুরে তাককা হুরে
বোঙা আদিবাসী দেবতা-অপদেবতার সর্বনাম। দুর্গা বাঙালির আবহমানের দুর্গতিনাশিনী। তারই কোমর জড়িয়ে নাচছে হাজত থেকে ছাড়ান-পাওয়া প্রৌঢ় নদী, কাঁধে শহর-পুরুষের গামছা। তাককা হুরে, আরে হুরে তাককা হুরে, শহুরে মাস্তানদের উল্লাসধ্বনি।
ভাঙনের ছায়াগাছ। এই ভাঙনকে সর্বদা দেখতে পাওয়া যায় না, অথচ সে তার কাজ করে চলেছে। ভাঙন বস্তুত একটি সার্বিক প্রক্রিয়া। এর দরুন সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে মজাদার মিলমিশ। বুর্জোয়ার বক্তব্য আশ্রয় করে লুমপেনের ভাষাকে।লুমপেন অ্যাডপ্ট করে বুর্জোয়ার চালচলন। এর সংস্কৃতি ঢুকে পড়ে ওর উঠোনে। ওর 'রোনাধোনা'য় শোনা যায় এর অনুরণন।
চিৎকার করতে-করতে পড়ছে জলপ্রপাত চুলে
ঢাউসপেট পোয়াতি অফিস-বারান্দায় আইল হাতে
থ্যাতলানো ট্যাক্সিচালক হাওড়া স্টেশানে
যেখানে সাপের ফণা জমা রাখতে হয়
শহর বিষদাঁত খুলে নেয় প্রত্যেকের। ছোবলানো তো চলবেই না, ফোঁস করাও নয়। অফিস বারান্দায় ফাইল হাতে গর্ভিনী। কী প্রসব করতে চলেছে সে ? তারই মধ্যে ঝরে যেতে থাকা কেশপাশের চিৎকার। আলুলায়িত কেশপাশ বাঙালির আবহমানের সৌন্দর্য-মিথের অংশ।
মেঝেময় ছড়িয়ে-থাকা গোঙানির টুকরো তুলে
তারা বদলায়নি তবু আদল পালটেছে
হে নাইলন দড়ি বাড়িতে এখন কেউ নেই
কিন্তু বাইরে হাজার দুর্গন্ধে ভাগ-করা শহর
কবিতাটি পড়তে-পড়তে বহু পুরোনো টার্কিশ ফিলম 'কংকারার্স অফ দি গোলডেন সিটি'র কথা মনে পড়ে। নিষ্পাপ একটি গ্রাম্য পরিবার শহরে এসে সব কিছু ধিরে-ধিরে হারাল। তার মেয়েরা হয়ে গেল বেশ্যা, পুরুষেরা অপরাধি। হাজার দুর্গন্ধে ভাগ-করা শহর--- গোল্ডেন সিটি। সোনার শহর। নারকেল দড়ির বদলে নাইলন দড়ি, সভ্যতার অগ্রগতি। বাড়িতে কেউ নেই , শূন্যতা অপরিসীম।
কবিতাটির শেষ স্তবকে এসে মলয় দুর্বার ছুট লাগান--- এমন ছুট যে কবিতা ব্যাপারটাই দুমড়ে-মুচড়ে যায়।
কচি বালক-পাছার নধরমাংস দেবদূত
মাখনমাখা ব্রয়লার যার শেষ খদ্দের
চলে গেছে তিন বছর তার ব্লাউজে সেফটিপিনগাঁথা হৃদয়
স্লুইস দরজা খুলে আলোর নারীশরীর
যে জীবন বুকের সামনে উঁচিয়ে অচেনা পিস্তল
তখনই সিঁড়িতে সাদা ছড়ির আওয়াজ তুলে
গামছায় মুখ ঢেকঢ গাঁও বালিকার কান্না
কেঁপে উঠেছে শিশুর গায়ে হাত ঠেকলে
ভাঙন যখন সব কিছুকেই ভাঙছে, তখন কবিতাকেও সে ভাঙবে। ভাঙতে-ভাঙতে কবিতাও মুক্ত হয়ে যাবে। তখনই বোধহয় বিদ্যুৎ ঝলকের মত এক অন্য কবিতার সৃষ্টিমুহূর্ত।'ভাঙনের ছায়াগাছ' কবিতায় আমরা সেই প্রক্রিয়াটি দেখতে পাচ্ছি, চাক্ষুষ।মলয় রায়চৌধুরী থেকে বোধ হয় এক নতুন কবিকুলের সৃষ্টি হল, যাঁরা কেবল কবি নন, আপোষহীন সামাজিক ভাষ্যকারও বটে।





 মুনিরা চৌধুরী | 122.179.172.247 | ৩০ আগস্ট ২০২১ ১২:৪৮
মুনিরা চৌধুরী | 122.179.172.247 | ৩০ আগস্ট ২০২১ ১২:৪৮