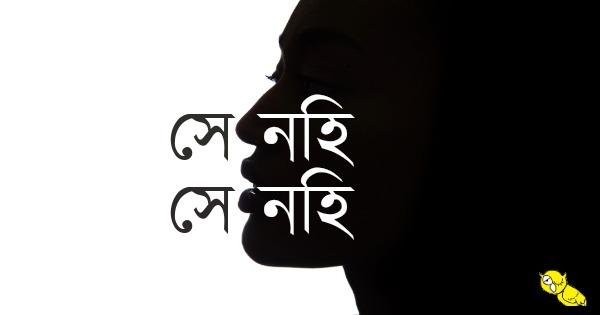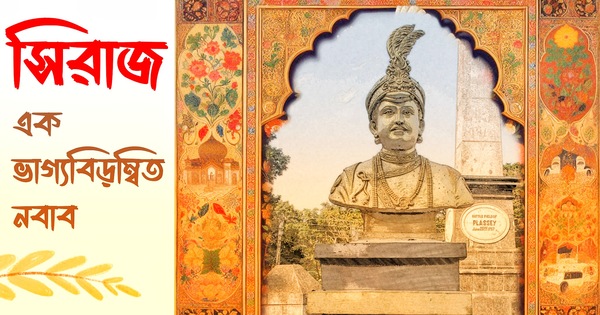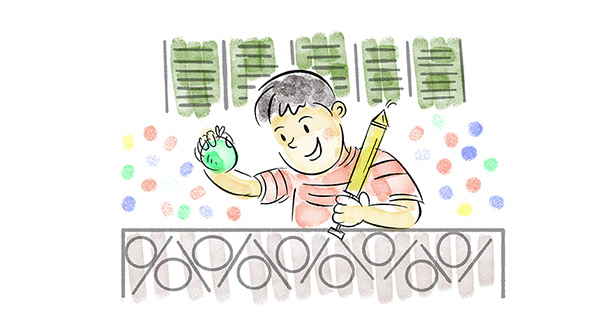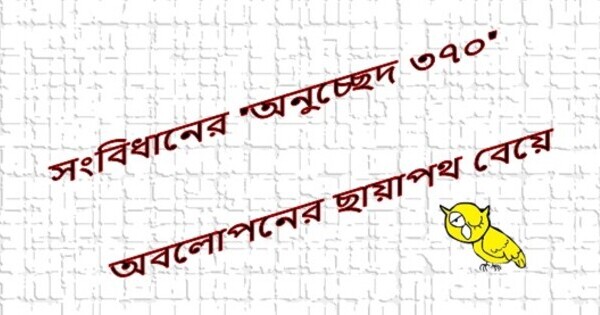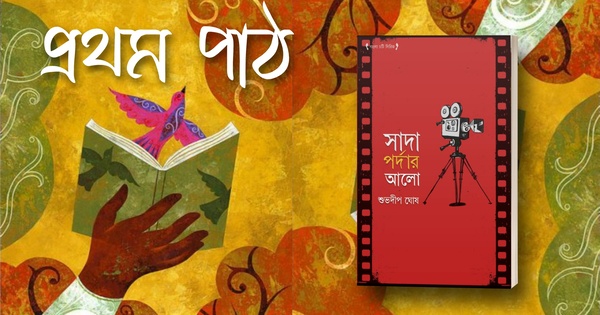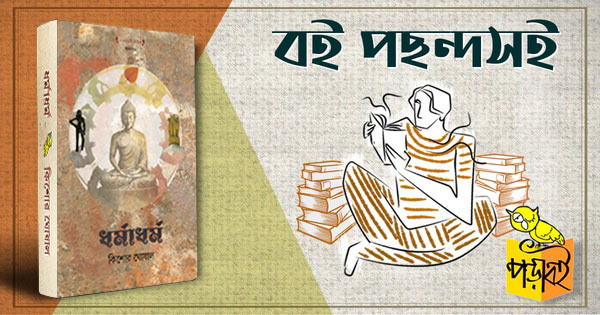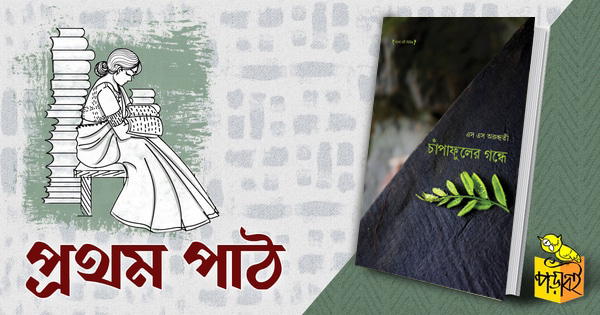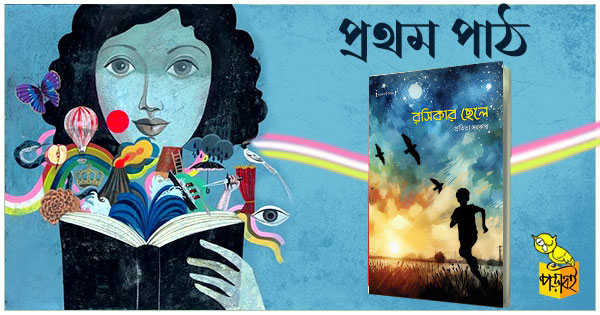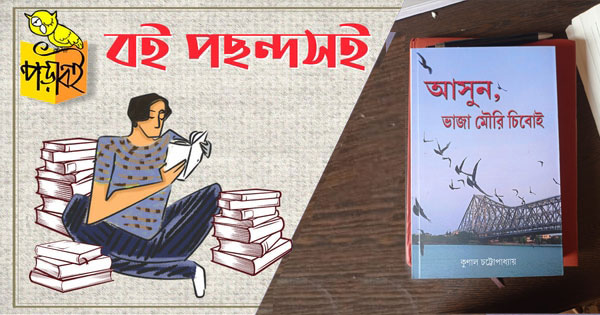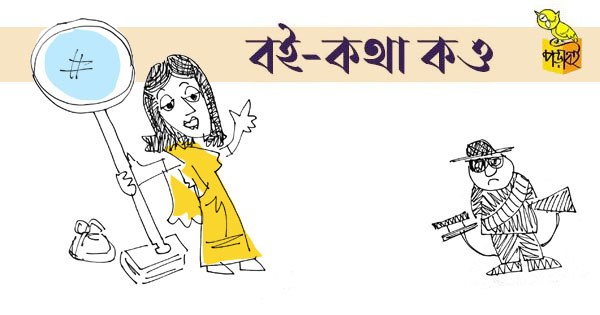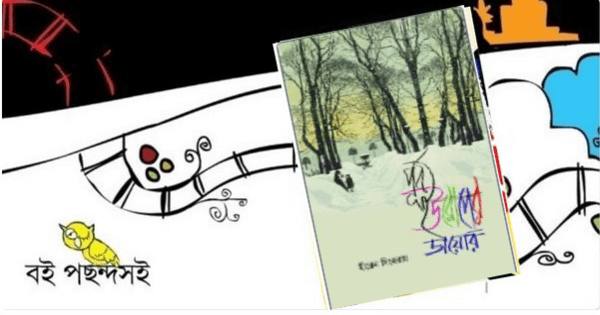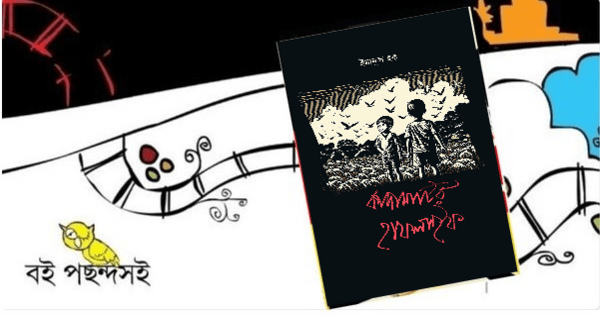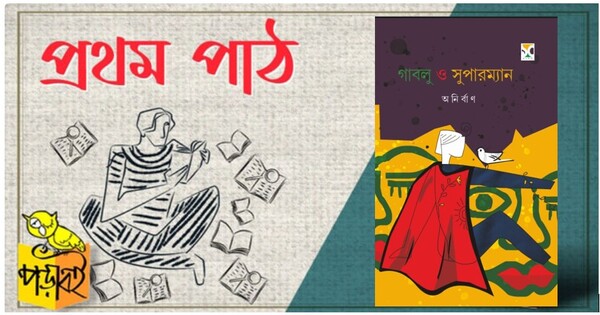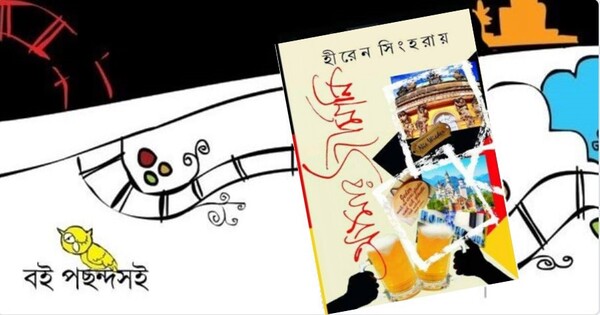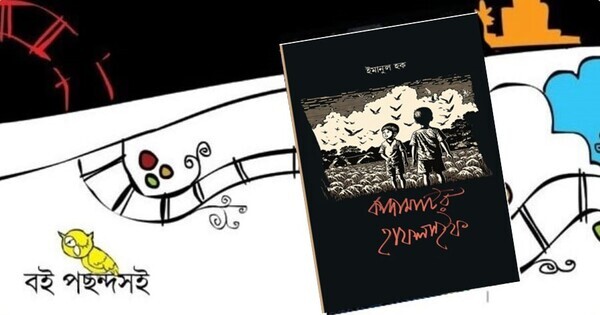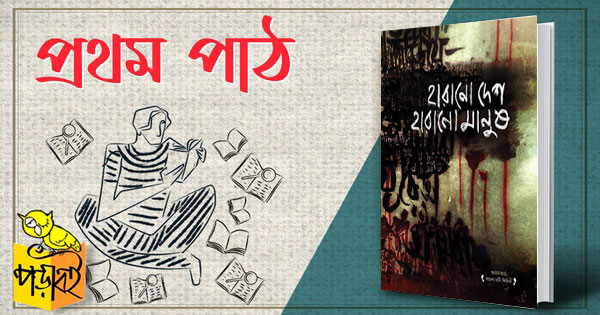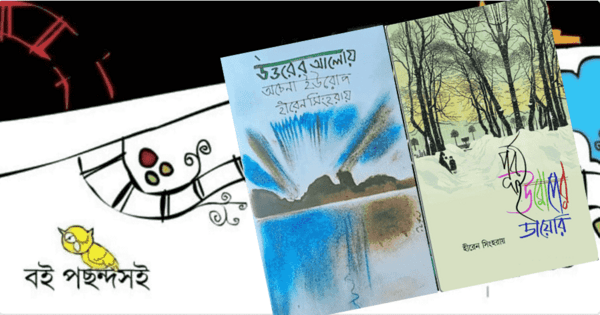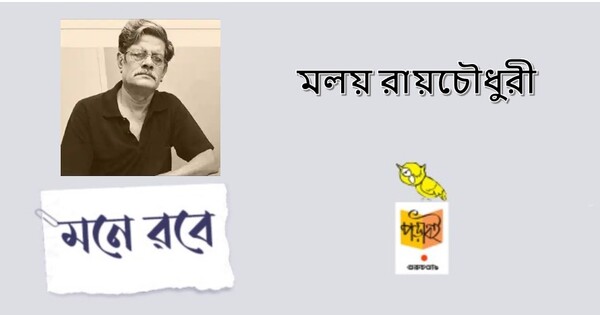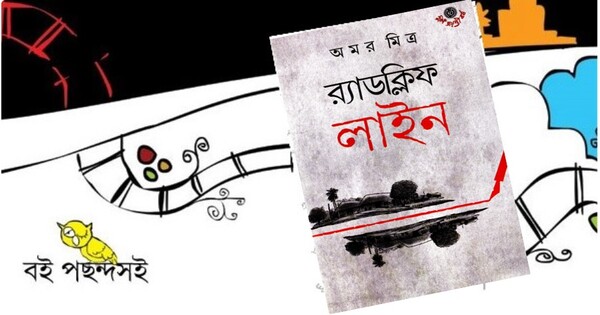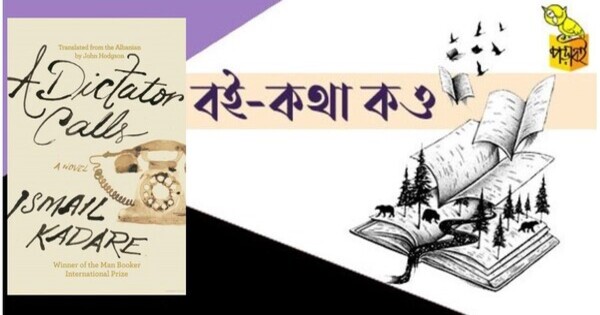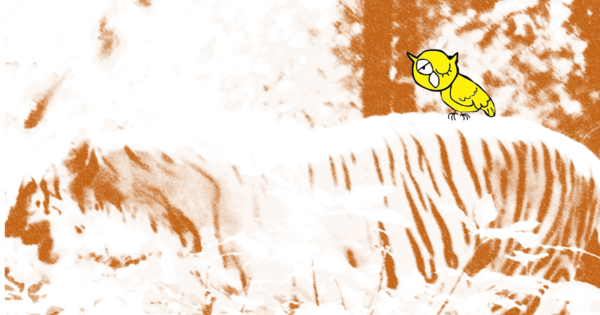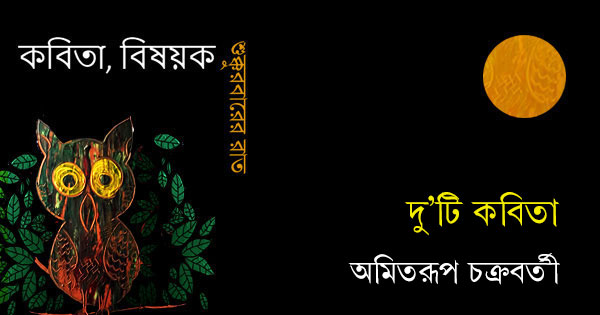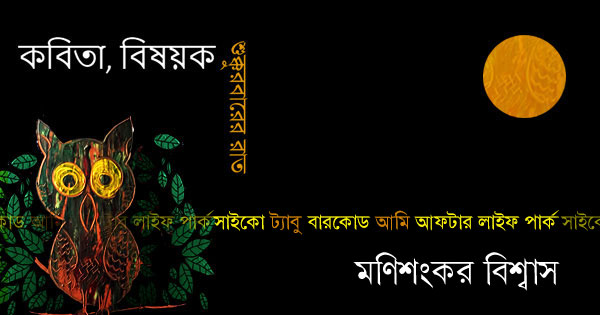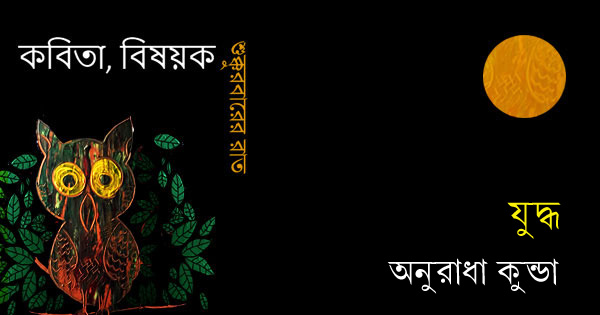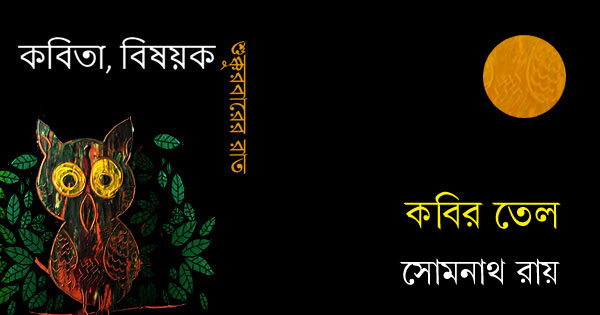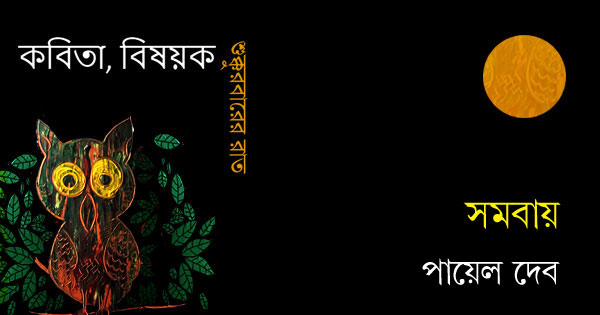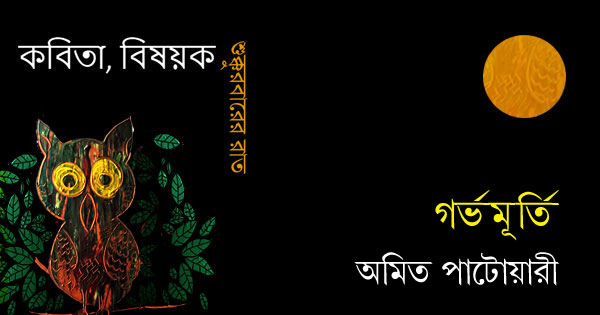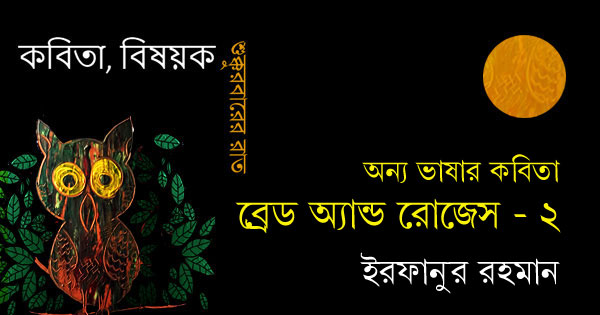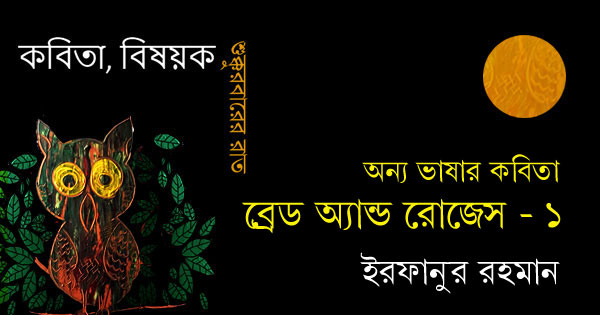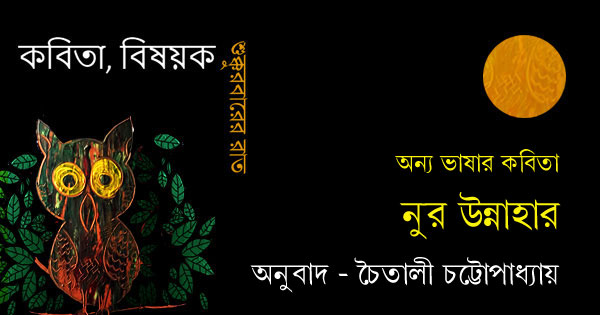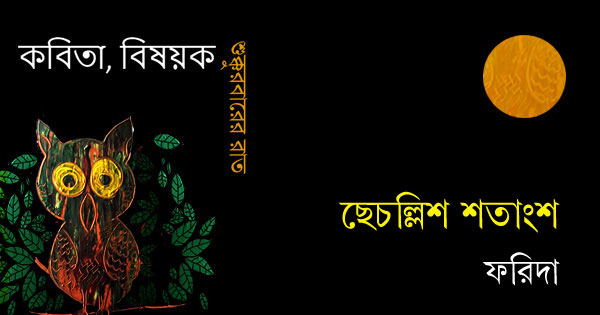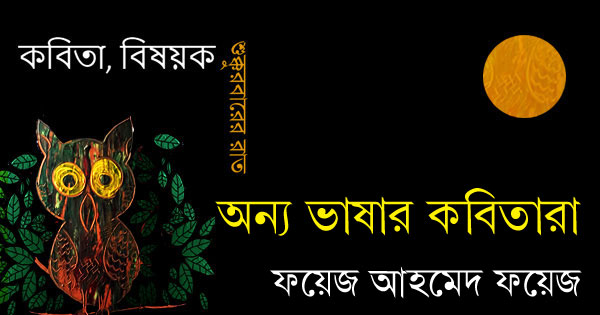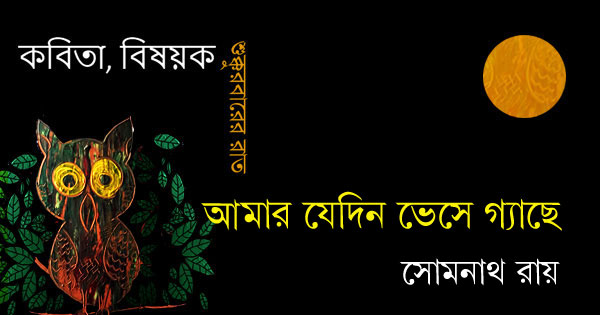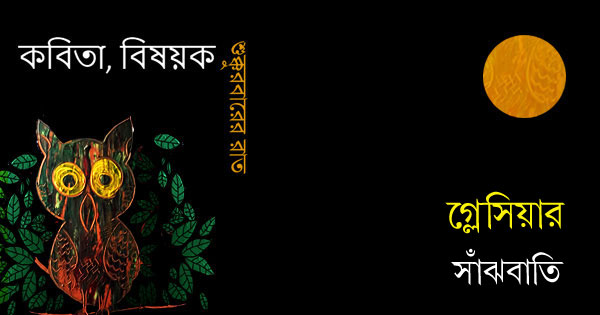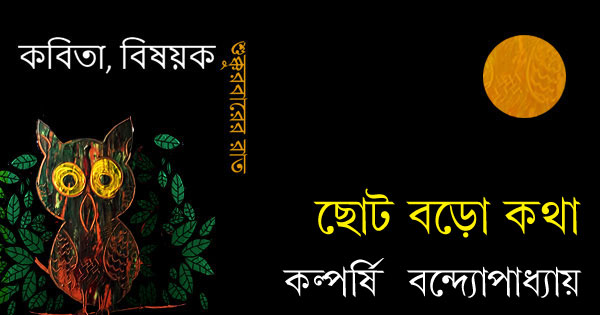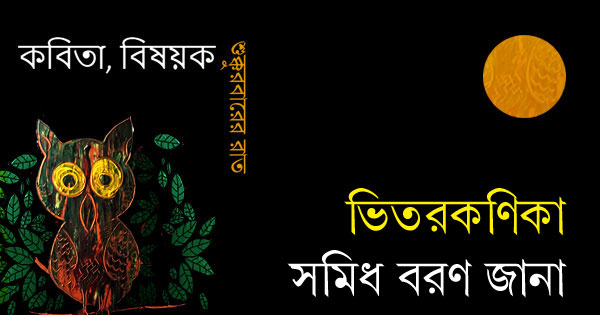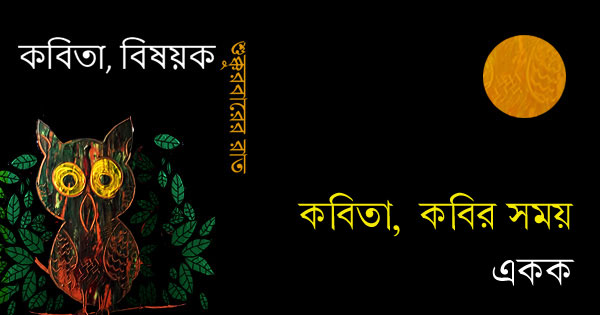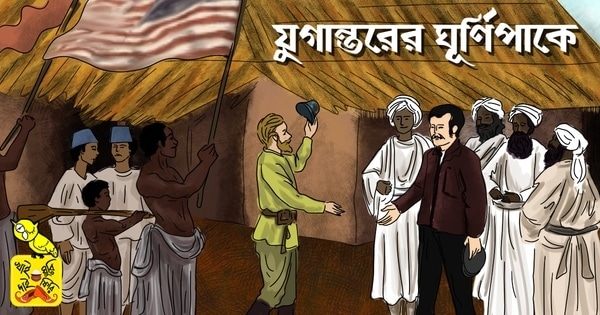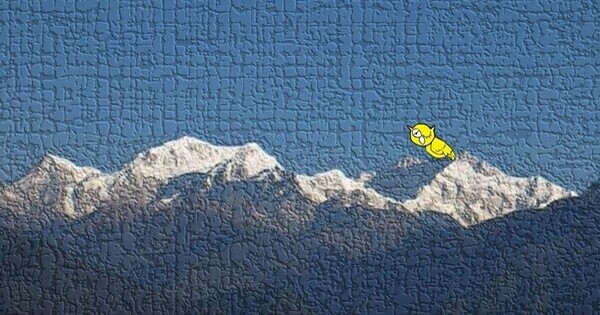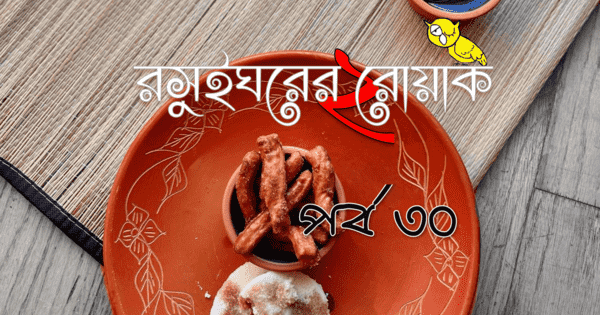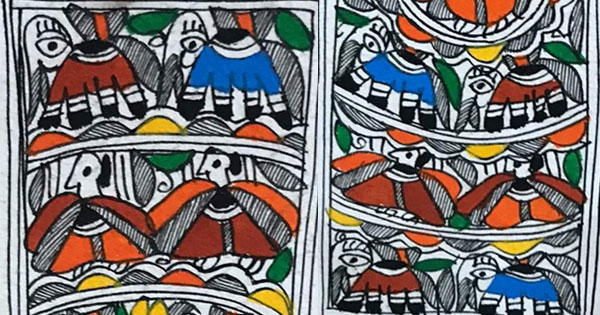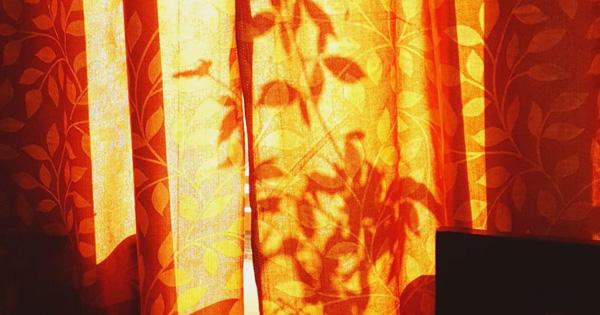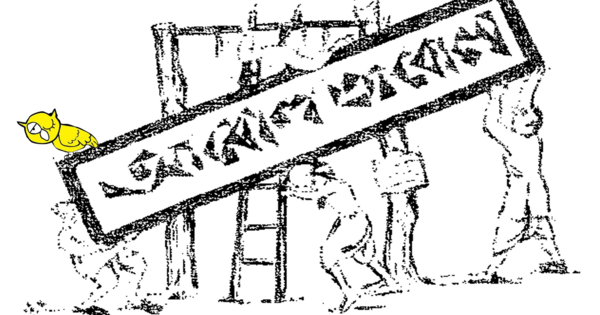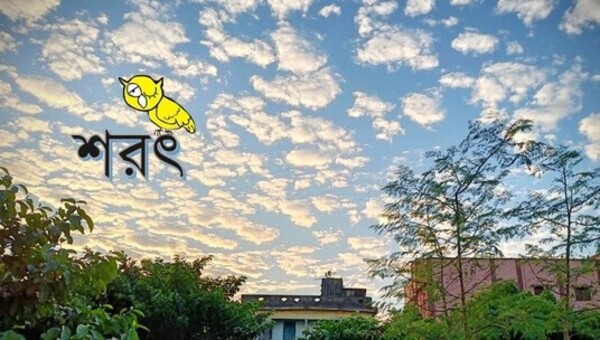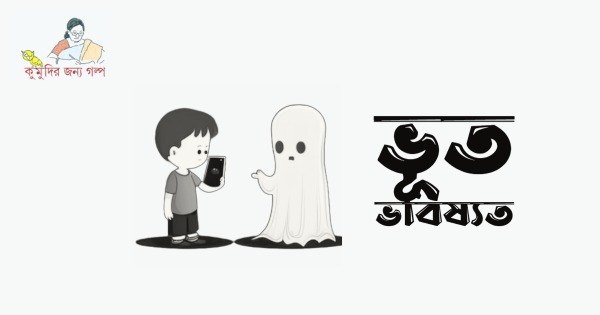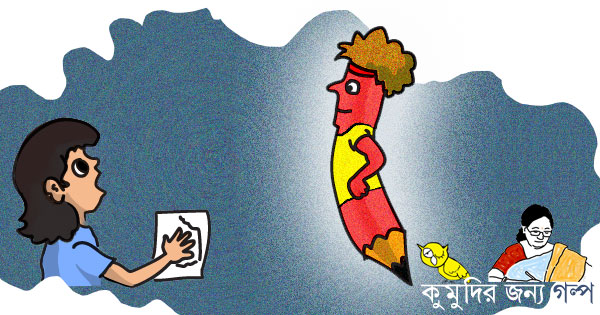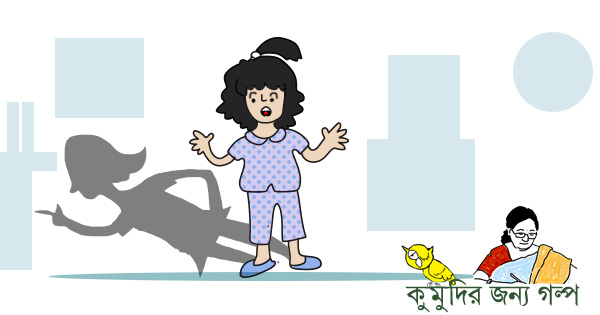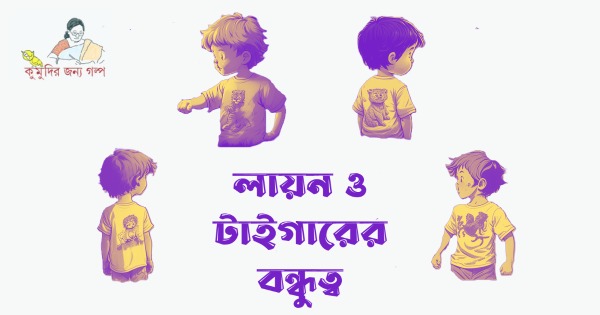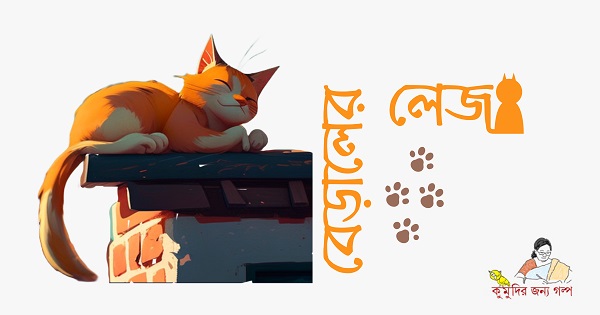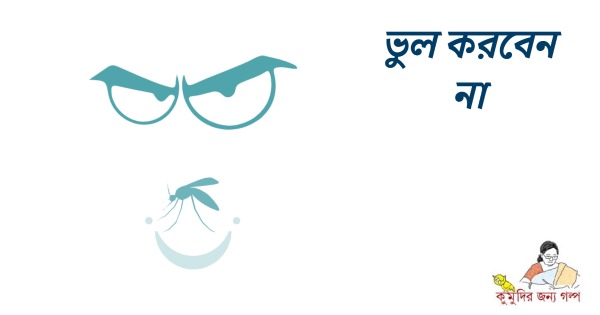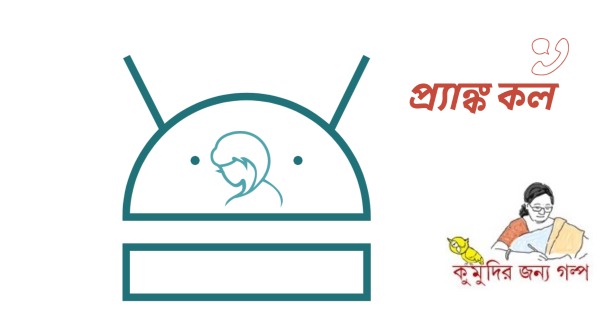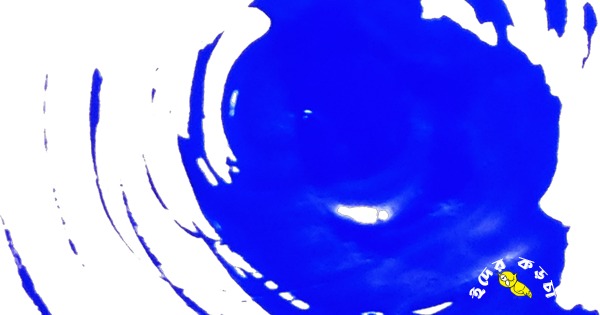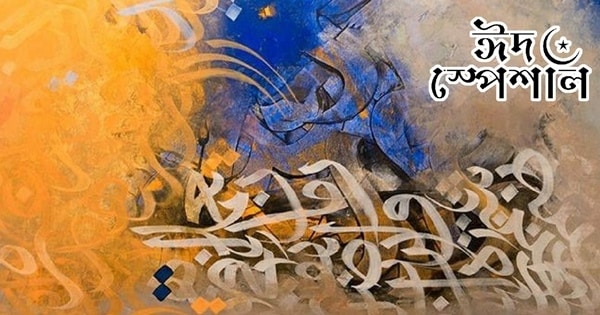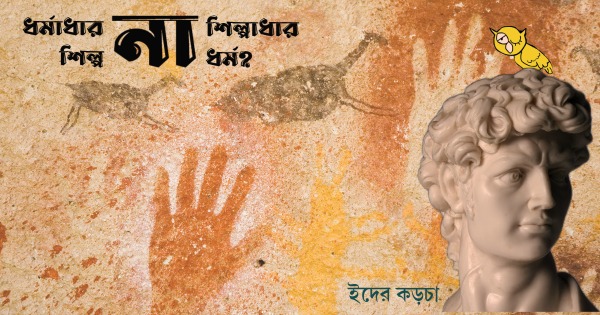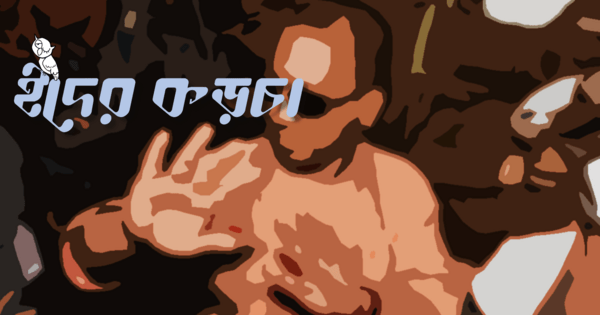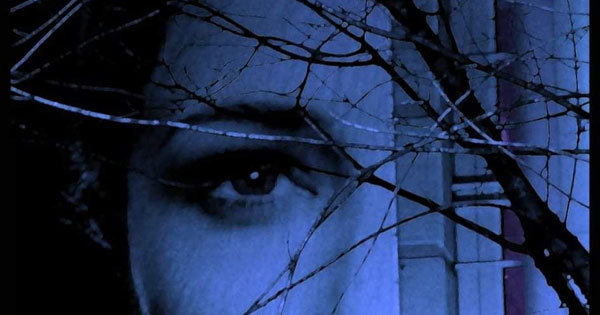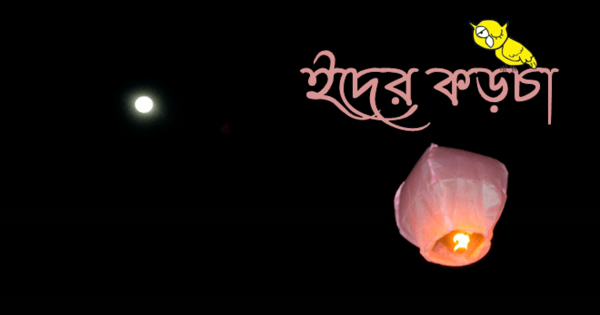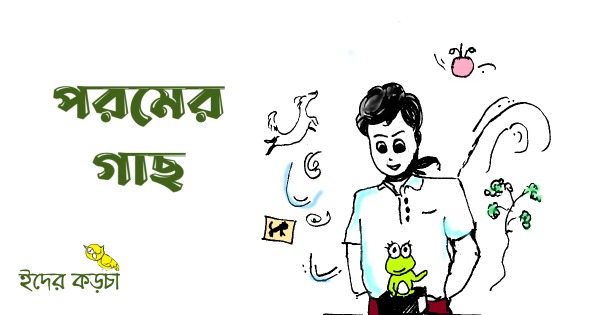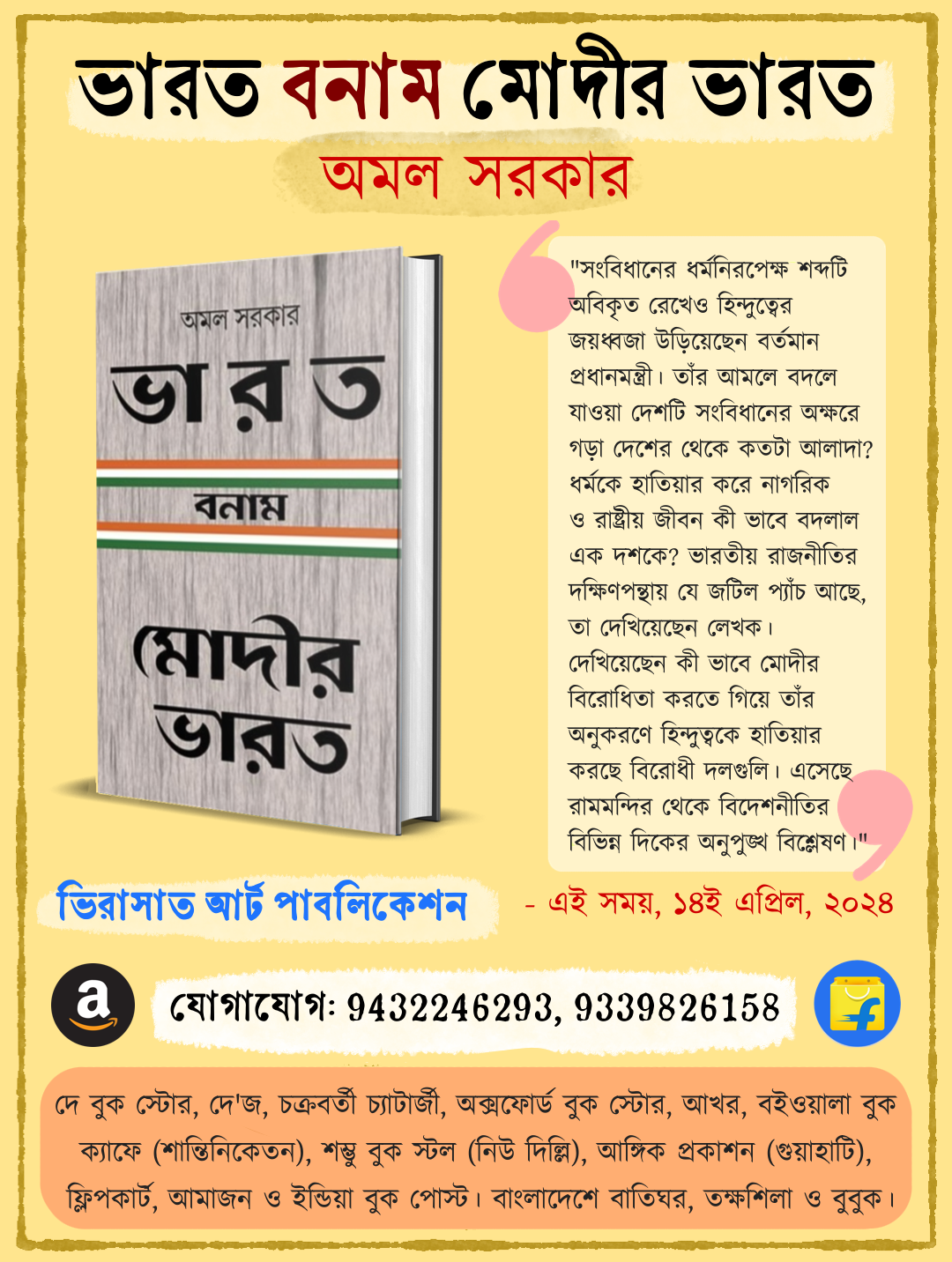তাজা বুলবুলভাজা...
সিএএ-র ফাঁদে মতুয়ারা - শান্তনীল রায় | ছবি: রমিত চট্টোপাধ্যায়বাংলার উদ্বাস্তু প্রধান এলাকাগুলিতে কান পাতলেই শোনা যায় নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে নানা গুঞ্জন। চব্বিশের লোকসভা ভোটে এই অঞ্চলগুলিতে জিততে বিজেপির মাস্টার্স স্ট্রোক এই নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ)।বিজেপি বারবার করে বলছে, সিএএ নাগরিকত্ব প্রদানের আইন, নাগরিকত্ব হরণের নয়। আর সেই আশাতেই বুক বেঁধেছে এক বিরাট সংখ্যক উদ্বাস্তু মানুষ। সিএএ-র বিষয়ে সম্যক ধারণা ছাড়াই। তবে দেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত সাহ দেশবাসীকে যেভাবে ক্রোনোলজি বুঝিয়েছিলেন, তা থেকে অতি সহজেই অনুমান করা যায় যে বিজেপির মনোবাসনা কেবল সিএএ -তে থেমে থাকবার নয়। প্রথমে সিএএ, তারপর এনআরসি (জাতীয় নাগরিক পঞ্জী)। আর যার পরিণতি হতে পারে উদ্বাস্তুদের জন্য ভয়ানক।উদ্বাস্তু মতুয়াদের নি:শর্ত নাগরিকত্বের দাবি আজকের নয়। বিজেপি ২০০৩ সালে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে আসলে, ভিটে ছেড়ে একবার বে-নাগরিক হওয়া কোটি কোটি উদ্বাস্তু মানুষের নাগরিকত্ব পুনরায় প্রশ্নের মুখে পড়ে। ২০০৪ সালে নাগরিকত্বের দাবিতে তারা সেসময় প্রথম আন্দোলনে নামে। নাগরিকত্বের ইস্যুতে মতুয়াদের প্রথম আন্দোলন ছিলো বিজেপির বিরুদ্ধেই। বাংলার সাম্প্রতিক রাজনীতিতে মতুয়া তথা নম:শূদ্র সম্প্রদায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর। এই প্রান্তিক উদ্বাস্তু মানুষদের প্রতি সিপিআইএমের দীর্ঘ উদাসীনতাই মমতা ব্যানার্জিকে তাদের কাছে আসার সুযোগ করে দিয়েছিলো। তিনি বুঝেছিলেন, উদ্বাস্তু প্রধান অঞ্চলগুলিতে জিততে হলে প্রয়োজন ঠাকুরবাড়ির সমর্থন। এর জন্য তিনি দুটো কাজ করেন। এক, ঠাকুর বাড়ির সাথে যোগাযোগ বাড়ান; দুই, উদ্বাস্তু মতুয়াদের নাগরিকত্বের সমস্যার সমাধানের আশ্বাস দেন। ফলস্বরূপ ঢেলে মতুয়া ভোট পায় তৃণমূল। কপিলকৃষ্ণ ঠকুরকে মন্ত্রী করা হয়। কিন্তু সমস্যা সমস্যা হয়েই থেকে যায়।এরপর মতুয়া ভোটকে কুক্ষিগত করতে কয়েক বছরের মধ্যেই মাঠে নামে বিজেপি। মতুয়াদের কাছে বিজেপির নানান প্রতিশ্রুতির মধ্যে প্রধান হয়ে ওঠে নাগরিকত্ব প্রদানের প্রতিশ্রুতি। ২০১৯ -এর লোকসভা ভোটের আগে মতুয়া ভোটকে নিজেদের দিকে টানতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বাংলাদেশের ওরাকান্দিতে অবস্থিত মতুয়াদের মূল ধর্মীয় মন্দিরে ভ্রমণ করেন। বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব একাধিকবার জনসভা করেন ঠাকুরনগরে। বকলমে কথা দেন তাঁরা নাগরিকত্বের জট কাটাবেন। আর সেই আশাতেই এক বড়ো অংশের মতুয়া ভোট বিজেপির দিকে ঘুরতে থাকে। আশা একটাই -নি:শর্ত নাগরিকত্ব। কিন্তু সিএএ কি সত্যিই তাদের নি:শর্ত নাগরিকত্ব দেবে? উত্তর হলো – একেবারেই না। সিএএ শর্তসাপেক্ষ নাগরিকত্ব প্রদানের কথা বলে। দু-হাজার চোদ্দো সালের একত্রিশে ডিসেম্বরের আগে পর্যন্ত বাংলাদেশ, পাকিস্তান এবং আফগানিস্থান থেকে ধর্মীয় নিপীড়নের কারনে পালিয়ে আসা হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পার্সি ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের শরনার্থীদের বিভিন্ন শর্তে নাগরিকত্ব প্রদান করবে কেন্দ্র। ধর্মের ভিত্তিতে নাগরিকত্ব প্রদান ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ ভারতবর্ষে এই প্রথম। নির্দিষ্ট ধর্মের প্রতি রাষ্ট্রের এই নির্বাচিত সহৃদয়তার আইনি স্বীকৃতি এক কথায় নজিরবিহীন। নাগরিকত্বের আবেদনের জন্য চোদ্দো সালের একত্রিশে ডিসেম্বর পর্যন্ত যে সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে তা নিয়েও রয়েছে প্রশ্ন। কারণ এরপর সে-সব দেশের সংখ্যালঘুদের উপর যে কোনো অত্যাচার হবে না, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। সিএএ -র অধীনে নাগরিকত্বের আবেদন করতে গেলে একজন উদ্বাস্তুকে প্রমান করতে হবে যে সে আদতেই বাংলাদেশ, পাকিস্থান বা আফগানিস্থানের নাগরিক। প্রমাণ হিসেবে দেখাতে হবে ওই তিনের কোনো একটি দেশের সরকার প্রদত্ত পরিচয় পত্র, পাসপোর্ট, জমির দলিল, স্কুল-কলেজের সার্টিফিকেট ইত্যাদির কোনো একটি। অথবা ভারতে প্রবেশের সময় বর্ডার থেকে দেওয়া বর্ডার স্লিপ। কিন্তু শরণার্থী মানুষদের বেশিরভাগেরই সেসব কাগজ নেই। কেনো নেই সে প্রশ্ন অবান্তর। তাছাড়া, অন্য দেশের সরকার প্রদত্ত সার্টিফিকেট, পাসপোর্ট, দলিল ইত্যাদির সত্যতা ভারত সরকার যাচাই করতে পারে কি? সেক্ষেত্রে সাহায্য নিতে হবে সেসব দেশের। কিন্তু বাংলাদেশ সরকার ইতিমধ্যে জানিয়েছে যে ধর্মীয় নিপীড়নের কারণে তাদের দেশের একজন নাগরিকও ভারতে আসেনি। তাহলে উদ্বাস্তুদের দ্বারা প্রদান করা কাগজের সত্যতা যাচাই হবে কীভাবে? উনিশ সালের সাতই জানুয়ারি জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কমিটি সিএবি (নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল) সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট পার্লামেন্টে পেশ করেছিলো। ঐ রিপোর্ট অনুযায়ী, ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো কমিটিকে জানিয়েছে, ৩১,৩১৩ জন শরণার্থী যারা ভারত সরকারের কাছে নাগরিকত্বের আবেদন করেছিলো এবং ভারত সরকার যাদের দীর্ঘ মেয়াদি ভিসা প্রদান করেছিলো, কেবলমাত্র তারাই এই আইন থেকে সুবিধা পাবে। তবে এই ৩১,৩১৩ জন আবেদনকারীর বেশিরভাগই বাংলার উদ্বাস্তু নয়। তাছাড়া গোটা দেশে উদ্বাস্তু মানুষের সংখ্যা কয়েক কোটি।সিএএ -র পোর্টালে করা আবেদনগুলি প্রথমে তদন্ত করবে নির্দিষ্ট জেলাস্তর কমিটির মাথায় থাকা ডেসিগনেটেড অফিসার। এরপর সে তার মতামতসহ আবেদনটিকে এমপাওয়ার্ড কমিটির কাছে পাঠাবে। কোনো ব্যক্তিকে নাগরিকত্ব দেওয়া হবে কিনা সেটা ঠিক করবে এই এমপাওয়ার্ড কমিটি। সম্প্রতি উনচল্লিশ পাতার নাগরিকত্ব সংশোধনী নিয়মাবলি প্রকাশ করেছে কেন্দ্র। সেই নিয়ম অনুযায়ী, একজন উদ্বাস্তুকে এফিডেভিট করে রাষ্ট্রকে জানাতে হবে যে সে বাংলাদেশ, পাকিস্তান অথবা আফগানিস্তানের নাগরিক। ধরে নেওয়া যাক, কোনো ব্যক্তি সিএএ -র আবেদন করলো এবং এফিডেভিটের মাধ্যমে লিখে দিলো, সে ভারতের নাগরিক নয়, বাংলাদেশ, পাকিস্তান অথবা আফগানিস্তানের নাগরিক। এবং প্রমাণপত্রের অভাবে বা অন্য কোনো কারণে এমপাওয়ার্ড কমিটি তার নাগরিকত্বের আবেদন খারিজ করে দিলো। পরবর্তীতে কেন্দ্র এনআরসি নিয়ে আসলে ওই বে-নাগরিক হওয়া ব্যক্তির ভবিষ্যৎ কী হবে? বেশিরভাগ উদ্বাস্তু পরিবারেরই ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ইত্যাদি রয়েছে৷ সিএএ এবং এনআরসি-র মাধ্যমে বেনাগরিক প্রমাণ হলে সে-সব যে বন্ধ করে দেওয়া হবে, তা বলাই বাহুল্য। অন্তত আসামের চিত্র তাই বলে। এই পরিস্থিতিতে সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করা অথবা রেশনের চালে সংসার চালানো মানুষদের কী হবে? নাকি ডিটেনশন ক্যাম্পই এদের আগামী ভবিষ্যৎ? প্রশ্নগুলো ঘিরে রয়েছে কেবলই ধোঁয়াশা। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশঙ্কায় ইতিমধ্যেই আত্মহত্যা করেছে বাংলার এক যুবক। তার পরিবারের লোক জানিয়েছে, সিএএ তে আবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় ‘কাগজ’ না থাকায় ভয়ঙ্কর আতঙ্কে ছিল বছর একত্রিশের দেবাশিস সেনগুপ্ত। দেশ থেকে বিতাড়িত হওয়ার ভয়েই আত্মহননের পথ বেছে নেয় সে। উদ্বাস্তুরা উপার্জন ও ব্যয় উভয়ই এই দেশে করে থাকে। ফলে ভারতবর্ষের জিডিপিতে তাদের সম্পূর্ণ অবদান রয়েছে। কিন্তু আগামীতে এই কোটি কোটি উদ্বাস্তুকে ডিটেনশন ক্যাম্পে কয়েদিদের মতো রাখলে, এক বিপুল অর্থের বোঝা দেশের উপর পড়বে – একথা বলাই বাহুল্য। সরকারি সার্টিফিকেট যেমন ভোটার কার্ড, আধার কার্ড ইত্যাদির তৈরির ক্ষেত্রেই ভুরিভুরি ভুলের অভিযোগ ওঠে, সেখানে এত এত মানুষের নাগরিকত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে উক্ত কমিটির যে ভুল হবে না, তা বলা যায় না। আমরা আসামের মানুষের এনআরসি সংক্রান্ত তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা ইতিমধ্যেই জানি। সেখানে এনআরসির সর্বশেষ তালিকা বের হওয়ার পূর্বে দুটি ভুলে ভরা খসড়া তালিকা প্রকাশ করা হয়। সর্বশেষ তালিকাটিও যে নির্ভুল একথাও অনেকে বিশ্বাস করতে নারাজ। এমত অবস্থায় কোটি কোটি উদ্বাস্তু মানুষের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ প্রশ্নের মুখে। শিক্ষাহীন, মানহীন মতুয়া সমাজকে একসময় শিক্ষা ও সম্মানের জীবন দানের জন্য নিরলস আন্দোলন করেছিলেন গুরুচাঁদ ঠাকুর। বলতেন, “খাও না খাও, ছেলেমেয়েকে স্কুলে পড়াও”। ভরসা সেই ‘ঠাকুর’ পদবিতে। তাই শান্তনু ঠাকুরের কথাতেই আস্থা রেখেছিলো মতুয়া জনগোষ্ঠির বিপুল সংখ্যক মানুষ। এমনকি টাকার বিনিময়ে তিনি তাঁর স্বাক্ষর করা ‘মতুয়া কার্ড’ বিলি করেছিলেন মতুয়াদের মধ্যে। ওই কার্ড দেখালেই নাকি পাওয়া যাবে নাগরিকত্ব! সহজ, সাধারণ মানুষেরা সেটাই মেনে নিয়েছিলো।সিএএ -কে সামনে রেখে দু'হাজার উনিশ সাল থেকে বাংলার পাঁচটি উদ্বাস্তু প্রধান লোকসভা এবং সাতাশটি বিধানসভা আসনে বিজেপি ভালো ফল করে আসছে। আগামী লোকসভা ভোটও লড়বে এই ইস্যুকে সামনে রেখে। কিন্তু নরেন্দ্র মোদি ও শান্তনু ঠাকুরকে বিশ্বাস করে মতুয়া সহ বাংলার অন্যান্য উদ্বাস্তুরা যে প্রতারিত হয়েছে, তাদের এই উপলব্ধি হওয়া এখন কেবল সময়ের অপেক্ষা। ************************তথ্যসূত্র: https://eisamay.com/west-bengal-news/24pargana-news/bjp-mla-asim-kumar-sarkar-opposes-new-matua-community-card-announced-by-mp-shantanu-thakur/articleshow/105538993.cmshttps://twitter.com/BanglaRepublic/status/1767893662539894828?t=qWkfn2RvaCfnrjjdqoHvSw&s=19https://bengali.abplive.com/videos/district/west-bengal-news-bjp-mla-asim-sarkar-himself-questioned-the-validity-of-matua-card-1027283https://bangla.hindustantimes.com/bengal/districts/citizenship-only-if-you-have-a-matua-card-shantanu-thakur-demand-resonates-with-tmc-bjp-31710407987896.htmlবিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে…….. - সোমনাথ গুহ | ছবি: রমিত চট্টোপাধ্যায়মার্চ ও এপ্রিল পরপর দু মাসে দুজন স্বনামধন্য সমাজ ও মানবাধিকার কর্মী দীর্ঘ কারাবাসের নরক-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়েছেন। গত ৭ই মার্চ অধ্যাপক জি এন সাইবাবা প্রায় এক দশকের কারাবাসের পর নাগপুর সেন্ট্রাল জেল থেকে মুক্তি পান। এর প্রায় এক মাস বাদে ভীমা কোরেগাঁও (বিকে) মামলায় ধৃত নারী ও দলিত অধিকার কর্মী, অধ্যাপক সোমা সেন জামিন পান। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর এই দুজনের মুক্তি অবশ্যই স্বস্তিদায়ক, কিন্তু যা ঢের বেশি অস্বস্তিকর তা হচ্ছে তাঁদের গ্রেপ্তার, তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাঁদের বিচার বা বিচার না-হওয়া পুরো বিচারব্যবস্থার স্বরূপকে নগ্ন করে দিয়েছে। সাইবাবার কাহিনি বহু চর্চিত, তবুও সেটাকে আমরা ফিরে দেখব এবং কোন কারণে অধ্যাপক সোমা সেন সহ ভীমা কোরেগাঁও মামলায় ধৃত অন্যান্যদের এতো বছর কারাবাস করতে হল, এবং কয়েকজনকে এখনো করতে হচ্ছে, সেটা বোঝার চেষ্টা করব। সাইবাবা আদিবাসীদের অধিকার সম্পর্কে সরব ছিলেন। ২০০৯ সাল থেকে শুরু হওয়া ‘অপারেশন গ্রীন হান্ট’ এর বিরুদ্ধে তিনি প্রবল ভাবে সোচ্চার হন। তাঁর বক্তব্য এই অভিযানের উদ্দেশ্য মধ্য ভারতের বিস্তীর্ণ আদিবাসী অঞ্চলের সম্পদ লুট করে তা কর্পোরেটদের হাতে তুলে দেওয়া। ২০১৪র মে মাসে মাওবাদীদের সাথে যুক্ত থাকার অভিযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং প্রায় এক বছর বাদে শারীরিক কারণে জামিন দেওয়া হয়। ২০১৫-১৬ সালে এর পুনরাবৃত্তি ঘটে। পরের বছর সিপিআই, মাওবাদীদের সাথে যুক্ত থাকার অভিযোগে তাঁকে ইউএপিএ নামক দানবীয় আইনের অধীনে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত করা হয়। সাইবাবা দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের রামলাল আনন্দ কলেজে ইংরাজির অধ্যাপক ছিলেন। ২০২১ সালে তাঁকে বরখাস্ত করা হয়। ২০২২ এর অক্টোবরে বম্বে হাই কোর্ট তাঁকে বেকসুর খালাস করে দেয়, বিচারপতিরা বলেন যে তাঁকে অভিযুক্ত করার জন্য যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়নি। কোর্ট সাইবাবা এবং তাঁর পাঁচ সাথিকে বেকসুর খালাস করার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে, মহারাষ্ট্র সরকার এই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে আবেদন করে। এরপরে শীর্ষ আদালত যে ভাবে শনিবার, একটা ছুটির দিনে বিশেষ বেঞ্চ গঠন করে তাঁদের মুক্তির ওপর স্থগিতাদেশ জারি করে তা এক কথায় বিস্ময়কর। আদালতের সময়সীমার বাইরে কোনও গুরুত্বপূর্ণ কারণে বিশেষ বেঞ্চ মিলিত হওয়া কোনও অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। সাংবিধানিক সংকট, ব্যক্তি স্বাধীনতা বা ফাঁসির আসামির আবেদন রদ করার শুনানি ইত্যাদি ক্ষেত্রে মধ্যরাতেও বিচারকরা মিলিত হয়েছেন। কিন্তু তথাকথিত একজন মাওবাদী, যিনি ৯০% প্রতিবন্ধি, যিনি ষোলোটি মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত, যাঁকে সামান্য দৈনন্দিন কাজ করতেও অন্যের সাহায্য প্রয়োজন হয়, তাঁর মুক্তি আটকাতে যেভাবে তড়িঘড়ি ব্যবস্থা নেওয়া হয় তাতে বিশিষ্ট আইনজ্ঞরাও স্তম্ভিত হয়ে যান। মাননীয় অধ্যাপকের আইনজীবী একটা অন্তিম চেষ্টা করেন, তিনি তাঁর মক্কেলের অসুস্থতার কারণে তাঁকে অন্তত কারাগার থেকে মুক্তি দিয়ে গৃহবন্দী রাখার আবেদন করেন। আদালত তাতেও আপত্তি করে, যুক্তি দেয় ঘরে বসেও তিনি নাশকতা মূলক কাজকর্ম করতে পারবেন, ফোনে কর্মীদের নির্দেশ দিতে পারবেন। প্রস্তাব দেওয়া হয় যে তাঁর ফোন বাজেয়াপ্ত করা হোক, নিষ্ঠুর আদালত তাতেও কর্ণপাত করতে অস্বীকার করে। এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে বিচারব্যবস্থা সাইবাবার মস্তিষ্ককে ভয় পায়। সেই অভুতপূর্ব স্থগিতাদেশের প্রায় ষোলো মাস পর সেই একই বম্বে হাই কোর্টের নাগপুর বেঞ্চ তাঁকে পুনরায় মুক্তি দেবার আদেশ জারি করে। আদালতের পর্যবেক্ষণ অত্যন্ত লক্ষ্যণীয়। তাঁরা বলেন অধ্যাপকের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অপ্রমাণিত অভিযোগ আনা হয়েছে এবং চক্রান্তের প্রস্তুতি হিসাবে তাঁর কাছে কোন নির্দিষ্ট উপাদান পাওয়া যায়নি। তাঁরা আরও বলেন কী ধরনের সন্ত্রাসবাদী কাজ তা ব্যাখ্যা না করার দরুন অভিযুক্তর বিরুদ্ধে মামলা দুর্বল। রাজ্য সরকার আবার শীর্ষ আদালতে আবেদন করে কিন্তু এবার তাঁরা স্থগিতাদেশ দিতে অস্বীকার করেন। আদালতের পর্যবেক্ষণ প্রমাণ করছে যে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ভুয়ো, সম্পূর্ণ মনগড়া যেটার ভিত্তিতে একজন গুরুতর অসুস্থ মানুষকে অন্তত সাত বছর ব্রিটিশ আমলের অন্ডা সেলে বন্দি করে রাখা হয়েছে। ক্যান্সারে আক্রান্ত বৃদ্ধা মাকে দেখার জন্য তাঁর জামিনের আবেদন বারবার নাকচ করা হয়েছে। মার মৃত্যুর পর শেষকৃত্যেও তিনি উপস্থিত থাকতে পারেননি, তখনো তাঁর জামিনের আবেদন নাকচ করে দেওয়া হয়েছে। এনআইএর মতে তিনি নাকি এতোই বিপজ্জনক যে কয়েক ঘণ্টার জন্য তিনি বাইরে এলেও তা রাষ্ট্রকে বিপন্ন করতে পারে। প্রক্রিয়াটাই যখন শাস্তিপ্রতিবাদী কন্ঠ দমন করার জন্য এটাই এখন রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোন বিচার ছাড়াই, শুধুমাত্র অভিযোগের ভিত্তিতে বছরের পর বছরের কাউকে কারাবন্দি করে রাখা। এর জন্য ইউএপিএ আইন হচ্ছে মোক্ষম হাতিয়ার যেটার লাগামছাড়া ব্যবহার হচ্ছে। ২০১৫ থেকে ২০২০ এই আইনে ৮৩৭১ জন ধৃত হয়েছেন, সাজা পেয়েছেন মাত্র ২৩৫ জন, ৩% এরও কম! ২০০৮, ২০১২, ২০১৯, বিভিন্ন সময়ে এই আইনকে সংশোধন করে আরও কঠোর, দানবীয় করে তোলা হয়েছে। এই আইন এক উলটপুরাণ যেখানে অভিযুক্তকেই প্রমাণ করতে হবে যে তিনি দোষি নন এবং এই আইনে জামিন দেওয়া নিয়ম নয়, সেটা ব্যতিক্রম; বিচারক এবং সরকারি কৌঁসুলি যদি মনে করেন অভিযুক্ত আপাত ভাবে নির্দোষ শুধুমাত্র তবেই জামিন দেওয়া যেতে পারে। এর সেরা উদাহরণ দিল্লি দাঙ্গা মামলায় অভিযুক্ত উমর খালিদ। ২০২০র সেপ্টেম্বরে উনি গ্রেপ্তার হয়েছেন, তারপর থেকে নানা অজুহাতে ওনার জামিনের শুনানি চোদ্দো বার মুলতুবি করা হয়েছে। ২০১৮র জুন মাসে অধ্যাপক সোমা সেন সহ আরও চারজন মানবাধিকার কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়। সোমা সেনের বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি নাকি সিপিআই মাওবাদী দলের সক্রিয় কর্মী, তিনি তাঁদের হয়ে তহবিল সংগ্রহ করতেন, হিংসাত্মক কার্যকলাপে ইন্ধন যোগাতেন এবং তিনি নাকি মাওবাদীদের বিভিন্ন ছদ্ম সংগঠনের সাথে যুক্ত। এছাড়া ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৭ পুনের কাছে ভীমা কোরেগাঁও-য়ে জনতাকে তিনি হিংসায় প্ররোচিত করেছিলেন। সোমা সেন সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেন এবং জানান যে ২০১৭র শেষ দিনে কোরেগাঁও-য়ে তিনি উপস্থিতই ছিলেন না। ডিসেম্বর ১৩, ২০১৮ তিনি প্রথম বার জামিনের আবেদন করেন। এরপর তাঁর আবেদন, এমনকি অসুস্থতার কারণে আবেদনও উপরোক্ত সব কারণের দরুন খারিজ করা হয়। অথচ আজ প্রায় ছয় বছর বাদে সুপ্রীম কোর্ট বলছে তাঁর বিরুদ্ধে যা প্রমাণ আছে তাতে আপাত ভাবে (প্রাইমা ফেসি) তিনি কোন সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে যুক্ত ছিলেন এটা প্রমাণিত হয় না। আদালত এটাও বলে তিনি কিছু সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং কিছু মহিলাকে সংগ্রামে উদ্দিপ্ত করেছেন বলেই তিনি মাওবাদী বা তাঁদের কোন ছদ্ম সংগঠনের সাথে যুক্ত ছিলেন এটাও প্রমাণিত হয় না। এছাড়া আদালত জানায় তৃতীয় কোন ব্যক্তির থেকে পাওয়া তথ্য বা উপাদান থেকে প্রমাণিত হয় না তিনি তহবিল সংগ্রহে যুক্ত ছিলেন। সোমা সেনের বিরুদ্ধে অভিযোগের যে কোন সারবত্তা নেই এই উপলব্ধিতে আসতে আদালতের প্রায় ছয় বছর লেগে গেল। ভীমা কোরেগাঁও বা দিল্লি ‘দাঙ্গা’ মামলায় এটাই হচ্ছে প্যাটার্ন! বছরের পর বছর অভিযুক্তদের কারাগারে বিনা বিচারে ফেলে রাখা হয়েছে, তারপর বহু টালবাহানার পরে কয়েকজনের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে প্রাইমা ফেসি এঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত নয়, এবং জামিন দেওয়া হয়েছে। বাকিরা তো এখনো জেলের ঘানি টানছেন। ছয় বছর হয়ে গেল বিকে মামলায় এখনো বিচারই শুরু হয়নি; শোনা যাচ্ছে চার্জশীটই নাকি ৫০০০ পাতা, ২০০ জন সাক্ষী। দিল্লি ‘দাঙ্গা’ মামলার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে কেউই পরিষ্কার নন। জামিনের শর্তাবলী এরপরেও আরও গল্প আছে। যাঁরা জামিন পাচ্ছেন তাঁদের মানমর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকাই দুরূহ হয়ে পড়ছে কারণ জামিনের শর্তাবলী ভয়ঙ্কর! সোমা সেনের জামিনের শর্তাবলী দেখা যাকঃ (১) পাসপোর্ট জমা দিতে হবে, (২) বিশেষ আদালতের অনুমতি ছাড়া তিনি মহারাষ্ট্রের বাইরে যেতে পারবেন না, (৩) যেখানে বসবাস করবেন সেখানকার নিকটবর্তি থানায় তাঁকে চোদ্দো দিন অন্তর হাজিরা দিতে হবে, (৪) মোবাইল সব সময় অন রাখতে হবে এবং ব্যাটারিতে চার্জ থাকতে হবে, (৫) জিপিএস অন রাখতে হবে এবং নিকটবর্তি এনআইএ অফিসারের ফোনের সাথে সেটি লিঙ্ক রাখতে হবে। শর্ত পালনে কোন বিচ্যুতি ঘটলে তৎক্ষণাৎ জামিন বাতিল হয়ে যাবে। সোমা নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজির অধ্যাপক ছিলেন, গ্রেপ্তার হওয়ার কয়েক দিনের মধ্যে তাঁকে বরখাস্ত করা হয়। তিনি কি অবসরকালীন সুযোগ সুবিধাগুলি পাবেন? আদালত নীরব। একই ভাবে সাইবাবা কি তাঁর চাকরি ফিরে পাবেন? এসব ব্যাপারে আদালত কোন নির্দেশ ব্যক্ত করেনি। বিশিষ্ট ট্রেড ইউনিয়ানিস্ট, আইনজীবী, সমাজকর্মী সুধা ভরদ্বাজ ২০২১ এর ডিসেম্বর মাসে বিকে মামলায় জামিন পান। তাঁর জামিনের ষোলোটি শর্ত আছে। সোমার ওপর যে শর্তগুলি চাপান হয়েছে সেগুলো তো আছেই আরও যা আছে তা হলঃ (১) তাঁকে মুম্বাই আদালতের এক্তিয়ারের মধ্যে থাকতে হবে এবং আদালতের অনুমতি ছাড়া এই চৌহদ্দির বাইরে তাঁর যাওয়া নিষেধ (অথচ তিনি দিল্লির ‘ন্যাশানাল ল বিশ্ববিদ্যালয়’-এর অধ্যাপক ছিলেন। সেটা তাঁর কর্মক্ষেত্র, সেখানে না গেলে তিনি জীবিকা অর্জন করবেন কী ভাবে?) (২) রক্তের সম্পর্ক আছে এরকম তিনজন আত্মীয়ের বাড়ি ও কর্মক্ষেত্রের ঠিকানা, ডকুমেন্ট সহ জমা দিতে হবে, (৩) মিডিয়ার কাছে তাঁর মামলা সংক্রান্ত কোন বক্তব্য রাখা নিষিদ্ধ, (৪) বিচারের সময় তাঁকে আদালতে উপস্থিত থাকতে হবে, তাঁর অনুপস্থিতির জন্য বিচার যেন বিলম্বিত না হয় (ছ বছরে বিচার শুরুই হয়নি!), (৫) বিকে মামলার অন্য সাথীদের সাথে যোগাযোগের কোন রকম চেষ্টা করবেন না, (৬) ঘনিষ্ঠ আত্মীয়রা ছাড়া তাঁর বাড়িতে অন্য ব্যক্তিদের জমায়েত নিষিদ্ধ ইত্যাদি। জামিনের ওপর স্থগিতাদেশ এই জমানায় মুক্তির আদেশের পরেও যখন স্থগিতাদেশ হতে পারে, তখন জামিনের ওপর তো হবেই। মহেশ রাউত, টাটা ইন্সটিটিউট অফ সায়েন্সের প্রাক্তনি এবং প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ উন্নয়নের ফেলো, জুন, ২০১৮ গ্রেপ্তার হন। ২০২৩ এর সেপ্টেম্বরে আদালত তাঁকে জামিন দেয়, বলে যে ইউএপিএ-তে তাঁর বিরুদ্ধে যা অভিযোগ আনা হয়েছে সেগুলো প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট উপাদান নেই। এনআইএ এর বিরুদ্ধে আবেদন করে এবং কয়েক দিনের মধ্যে আদালত নিজেদের রায়ের বিরোধিতা করে বলে তাঁর সাথে মাওবাদীদের যোগাযোগ পাওয়ার কারণে তাঁরা পুনর্বিবেচনা করে রায়ের ওপর এক সপ্তাহের স্থগিতাদেশ দিচ্ছেন। সেই এক সপ্তাহ এখনো চলছে! কোন না কোন অজুহাতে আজ পর্যন্ত সেই স্থগিতাদেশ বহাল আছে। একই ভাবে প্রসিদ্ধ মানবাধিকার কর্মী গৌতম নাভলাখা ডিসেম্বর ২০২৩ জামিন পান এবং প্রায় সাথে সাথেই এনআইএর আবেদনের কারণে আদালত জামিনের ওপর ছয় সপ্তাহের স্থগিতাদেশ জারি করে। এর মধ্যে শারীরিক অসুস্থতার কারণে কারাগার থেকে সরিয়ে তাঁকে গৃহবন্দি করা হয়। মজার ব্যাপার হচ্ছে গৃহবন্দিত্ব বা হাউস এরেস্টের কোন কনসেপ্ট ভারতীয় আইনে স্বীকৃত নয়। যেহেতু গৌতম নিজে গৃহবন্দি হওয়ার আবেদন করেছিলেন, তাই আদালত শর্ত দেয় যে গৃহবন্দিত্বের খরচ (সিসিটিভি লাগান, যাঁরা প্রহরায় থাকবেন তাঁদের পারিশ্রমিক ইত্যাদি) অভিযুক্তকেই বহন করতে হবে। শেষ যা জানা গেছে সেই খরচ নাকি প্রায় দেড় কোটিতে পৌঁছে গেছে। বর্তমানে এই খরচ নিয়ে এনআইএ এবং অভিযুক্তের আইনজীবীর মধ্যে দরাদরি চলছে। আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে চূড়ান্ত ভাবে হেনস্থা করা, বারবার বুঝিয়ে দেওয়া নিপীড়িত শ্রেণী, লিঙ্গ, জাতপাতের বিরুদ্ধে সরব হয়েছ তো তুমি শেষ। বনে জঙ্গলে খনন হচ্ছে, বড় বড় কর্পোরেট মাইনিং করছে সেটার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার, সংগ্রামি আদিবাসীদের পাশে দাঁড়ানর কোন অধিকার তোমার নেই। সোমা, সুধা, মহেশ, গৌতম এঁরা তো সমাজের প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি, আর যাঁরা নন? ২০২২য়ে ইউটিউবে ফাদার স্ট্যান স্বামীর ওপর একটি ভিডিওতে পারাকালা প্রভাকর জানাচ্ছেন ওই বছরের মার্চ মাসে ইউএপিএতে অভিযুক্ত ১২২ জন ১৯ বছর কারাবাসের পর মুক্তি পেয়েছেন। ভাবা যায়! এতগুলো বছরে তাঁদের নিয়মিত আদালতে যেতে হয়েছে, জেল থেকে থানায় যেতে হয়েছে। অরুণ ফেরেরা, কার্টুনিস্ট, বিকে মামলায় অভিযুক্ত ২০০৭ থেকে ২০১২ কারাবাস করেছেন, ২০১৮য় পুনরায় গ্রেপ্তার হয়েছেন এবং পাঁচ বছর বাদে মুক্তি পেয়েছেন। সেই মাওবাদী অভিযোগ, কিন্তু কোন কিছুই প্রমাণিত নয়। আমাদের রাজ্যে গৌর চক্রবর্তী সাত বছর ইউএপিএতে কারাগারে থাকার পর ২০১৬য় মুক্তি পেয়েছেন। এই তালিকার শেষ নেই, এই নরক-যন্ত্রণারও শেষ নেই।ইদবোশেখির লেখাপত্তর - গুরুচণ্ডা৯ | অলংকরণ: রমিত চট্টোপাধ্যায়শীতকাল বইমেলা হইচই-এর দিনকাল ফুরিয়ে এসে গেল শান্ত হয়ে বসে লেখালেখির কাল। বাইরে তাপমাত্রা বাড়ছে রোদ্দুরের জন্য, নির্বাচনের জন্য। সাথে কোথাও প্যাচপ্যাচে ঘাম তো কোথাও ঝরঝর বৃষ্টি। সন্ধ্যের আবছায়ায় দোকানে ভিড় জমায় সারাদিন রোজা রাখা ক্লান্ত মানুষ, গাজনের প্রস্তুতি নেওয়া শ্রান্ত মানুষ, চৈত্রসেলের হাতছানিতে মুগ্ধ মানুষ। টুপটাপ জমে ওঠে গল্পেরা, কবিতারা। নির্বাচনী জনসভার কোণাকাঞ্চিতে, ইফতারির থালার পাশে, গাজনের সন্ন্যাসীর ঝোলায় চুপটি করে অপেক্ষা করে তারা মানুষের জন্য। আমরা আপনাদের কাছে ডাক পাঠিয়েছিলাম তাদের খপ করে ধরে ফেলে, ঝপ করে লিখে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিতে। এসে গেছে তারা। আগামী কয়েকদিন ধরে রোজ দুটি-তিনটি করে তারা এসে হাজির হবে বুলবুলভাজার পাতায় - টাটকা ভাজা, গরমাগরম। পড়তে থাকুন। ভাল লাগলে বা না লাগলে দুই বা আরো অনেক লাইন মন্তব্য লিখে জানিয়ে দিন সে কথা। মন চাইলে, গ্রাহক হয়ে যান লেখকের। আর হ্যাঁ, আপনিও লেখা নিয়ে চলে আসুন গুরু আর চন্ডালের আড্ডা গুরুচন্ডা৯-র পাতায়।সূচীপত্রঃস্মৃতিচারণবর্ষশেষ, বর্ষশুরু: অমিতাভ চক্রবর্ত্তীও চাঁদ: সেমিমা হাকিমসারেতে থাই নববর্ষ: হীরেন সিংহরায়চান রাত: সাদেকুজ্জামানকাব্যজলের সমাধি: জগন্নাথ দেব মন্ডলগিরগিটি ও অন্যান্য কবিতা: ফরিদাসমুদ্রে সনেট: সোমনাথ রায়পাঁচটি কবিতা: অমিতরূপ চক্রবর্তীতিনটি কবিতা: অরিত্র চ্যাটার্জিউপগ্রহ: অমিত চট্টোপাধ্যায়আব্বু আব্বা বাবা: মাজুল হাসানশেষের কবিতা: দীপ্তেনকবিতাগুচ্ছ: মণিশংকর বিশ্বাসসিন্দবাদের গল্প ছড়ানো ছাদে: সুকান্ত ঘোষকবিতাগুচ্ছ: বেবী সাউগপ্পোখুচরো: সুমন মুখার্জীসুফি: আফতাব হোসেন রতন, দ্য ব্যাকবেঞ্চার: নরেশ জানাডাক দিয়ে যায়: এস এস অরুন্ধতীমহারাজ ছনেন্দ্রনাথ ও মার্কণ্ডেয়র চিঠি: রমিত চট্টোপাধ্যায়পাখির অন্তর্ধান রহস্য: মৃণাল শতপথীএই ঘুম শারীরবৃত্তীয়: দীপাঞ্জন মুখোপাধ্যায়ওয়েথসাম: উপল মুখোপাধ্যায়কোশিশ কিজিয়ে: কিশোর ঘোষালটুনিমুনির জীবন: দময়ন্তীদৌড়বাজ হাউসকীপার: সমরেশ মুখোপাধ্যায়হন্য: সৈয়দ তৌশিফ আহমেদসীমান্তরেখা: প্রতিভা সরকারসাদা খাম: দীপেন ভট্টাচার্যসুর: অনুরাধা কুন্ডাবুড়োশিবতলা: পায়েল চট্টোপাধ্যায়ইদ বৈশাখ মানে মা: ইমানুল হকউনিশে এপ্রিল: সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায়নভেলাফকির ফয়জুল্লাহ: মুরাদুল ইসলামনিবন্ধ আজ নববর্ষের আখ্যান: সোমনাথ মুখোপাধ্যায়
হরিদাস পালেরা...
দোলজ্যোৎস্নায় শুশুনিয়ায় - ৬ - সমরেশ মুখার্জী | বিবর্তনের ধারাসুমন বলে, "ধরতাইটা ভালো দিলি। স্বীকার করছি যা আলোচনা করতে যাবো তা নিয়ে আমার একটু সংকোচ ছিল কিন্তু তোদের কথায় তা কেটে গেল। তবে আমি হয়তো তোর মতো অতো গুছিয়ে বলতে পারবো না, আমার পড়াশোনার গণ্ডী সীমিত। তবু চেষ্টা করছি আমি যেভাবে ভাবি - বলতে। "দ্যাখ এটা স্বীকৃত সত্য যে বর্তমান মানুষ আদিমানবের রূপান্তরিত রূপ। সেই আদিমানব ছিল প্রাইমেটসদের সমগোত্রীয়। ওরাংওটাং এবং শিম্পাঞ্জি তাই বর্তমান মানুষের পূর্বপুরুষের নিকটতম প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য হয়। ট্রেনিং দিলে এরা মানুষের হাবভাব অনেকটা অনুকরণ করতে পারে। তবে আদিমানব ছিল পশুরই মতন। চার হাত পায়ে চলতো, কাঁচা মাংস, ফলমূল খেত। একদিন সে পেছনের দুপায়ে দাঁড়াতে শিখল। সামনের দুটো হাত শরীরের ভারবহন থেকে মুক্ত হয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে সৃজনশীল যন্ত্রে রূপান্তরিত হলো। তা আবিস্কার করলো আগুন, চাকা, লোহার ব্যবহার। এই তিনটি যুগান্তকারী আবিস্কার তাকে আর ফিরে তাকাতে দিল না। কয়েক কোটি বছরের বিবর্তনের পরে আজও গরু হাম্বা হাম্বা বা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে চলেছে কিন্তু মাত্র এক কোটি বছরের মধ্যে মানুষের অবিশ্বাস্য রূপান্তর হোলো। ফলে মানুষ যে কেবল পৃথিবীর তাবৎ প্রাণীকুল থেকে আলাদা হয়ে গেল তাই নয় তাদের ওপর কায়েম করলো নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রন। এতো অল্প সময়ে এহেন উত্তরণ কী ভাবে সম্ভব হোলো? বিবর্তনবাদে এই মিসিং লিঙ্ক বিশেষজ্ঞদের গবেষণার বিষয়, তা আমাদের এক্তিয়ারের বাইরে।"সুমন একটু থামে। এখন জোৎস্না উজ্জ্বল। তিনজন গভীর অভিনিবেশে তাকিয়ে আছে সুমনের দিকে। সুমন বলে চলে, "আদিমানবের আদিতেও ছিল কয়েক কোটি বছরের ক্রমবিবর্তনের ধারা। ফলে পশুসমাজের নানান প্রবৃত্তিগত বৈশিষ্ট্য আদিমানবের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছিল। বহু কোটি বছরের সঞ্চিত প্রবৃত্তিগত বৈশিষ্ট্য বা instictive characteristics মাত্র এক কোটি বছরের বিবর্তনের ফলে বিশেষ পরিবর্তিত হওয়া সম্ভব নয়। ফলে পশুসূলভ নানা প্রবৃত্তিগত বৈশিষ্ট্য বিবর্তিত মানুষের মধ্যেও সুপ্ত ভাবে রয়ে গেল।""তবে বুদ্ধি ও যুক্তিবোধের বিকাশের ফলে মানুষ বুঝতে শিখলো সমাজবদ্ধ জীবনে মানুষ কেবল প্রবৃত্তিগত তাড়নায় পশুর মতো আচরণ করতে পারে না। তৈরী হোলো আইন কানুন, বিধি-নিষেধ, প্রথা, লোকাচার। ঘোষিত হোলো সমাজে গ্ৰহণযোগ্য আচরণের প্রেক্ষিতে বিচ্যূতির শাস্তি। ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ সচেতন বিবেচনাবোধ ও সংযমী অভ্যাসে সমাজস্বীকৃত আচরণ করতে শিখলো। তাই ক্ষিধে পেলে ভিক্ষা চাওয়া যেতে পারে কিন্তু কেড়ে খাওয়া উচিত নয়। তবে অবচেতন মনে রয়ে যাওয়া অবদমিত প্রবৃত্তিগত বৈশিষ্ট্যের প্রভাবে কিছু আচরণ কখনো সচেতন মনের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। আর তখনই হয় সমস্যা। কখনো তা বাহ্যিকভাবে শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়ায় প্রকাশিত হয়। কখোনো তা চিন্তা ভাবনাকে প্রভাবিত করে।"প্রবৃত্তি ও প্রবণতা চুনি বলে, "বাব্বা, জেঠু! লোহা, সিমেন্ট, বালি ঘাঁটা সিভিল ইঞ্জিনিয়ার হয়ে তুইও তো দেখছি ঈশুর মতো গুছিয়ে কথা বলছিস! বিবর্তনের ফলে ক্রমশ তথাকথিত অর্থে উন্নত হয়েও মানুষের মধ্যে কেন কিছু পাশবিক প্রবৃত্তি রয়ে গেছে সেটা তো ভালোই বললি। কিছু উদাহরণ দিয়ে কী খোলসা করা যায়?"সুমন বলে, "ঠিক বলেছিস। যতই আমরা তাত্ত্বিক আলোচনা করি না কেন, উদাহরণ তা বুঝতে সাহায্য করে। যেমন ধর প্রাণীদের মধ্যে লড়াই মূলত হয় প্রজননের জন্য সঙ্গিনী নির্বাচন, দলের ওপর আধিপত্য কায়েম এবং এলাকার ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে। মাংসাশী প্রাণীর শিকার করা লড়াই নয় কারণ তা কেবল ক্ষুধার তাড়নায়। এছাড়া গোষ্ঠীবদ্ধ প্রাণী - যেমন হাতি বা সিংহ - দল থেকে বিতাড়িত হলে ক্ষিপ্ত হয়ে আক্রমণাত্মক হয়ে উঠতে পারে। তেমনি সন্তানের বিপদের আশাঙ্কায় মা পশুও রক্ষণাত্মক কারণে আক্রমণাত্মক হয়ে উঠতে পারে। এছাড়া পশুরা অহেতুক নিজেদের মধ্যে মারামারি, খেয়োখেয়ি করে শক্তি ক্ষয় করে না। একান্তচারী শ্বাপদ, যেমন দুটো পুরুষ বাঘও যদি আচমকা জঙ্গলে মুখোমুখি হয়ে যায় তাহলে তাদের প্রথম প্রবৃত্তিগত প্রতিক্রিয়া হবে পরস্পরকে এড়িয়ে যাওয়া। অর্থাৎ LIVE AND LET LIVE. তবে এই আপ্তবাক্য তারা দর্শনশাস্ত্র, গেম থিয়োরী ইত্যাদি ঘেঁটে শেখেনি। শিখেছে জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতায়।" "এবার দেখা যাক বুদ্ধিমান মানুষ কী করে। ভীড় বাসে অজান্তেই পা মাড়িয়ে দেওয়ার মতো তুচ্ছ ঘটনাতেও কথা কাটাকাটি থেকে খিস্তি খেউড়, হাতাহাতি হয়ে ব্যাপারটা হয়তো থানা পুলিশ অবধি গড়িয়ে গেল। তার ফলে হয়তো দুজনেই ভুগলো।" তুলি বলে, "কিন্তু জেঠু, এটা কী বুদ্ধিমান মানুষের পশুর মতো প্রবৃত্তিগত তাড়নায় আচরণের উদাহরণ হিসেবে ঠিক হোলো? তুই তো এইমাত্র বললি পশুরা ঝগড়াঝাঁটি, মারামারি করে না।"সুমন বলে, "তুলি, তুই একটা মোক্ষম ক্লু দিলি। এক্ষেত্রে তুইও একটি প্রবৃত্তিগত তাড়না, মানে কৌতূহল, দমন করতে পারিস নি। তাই আমি বক্তব্য শেষ করার আগেই পেশ করলি তোর প্রশ্ন। অবশ্য এ তাড়নাও দমন করা সহজ নয়।" তুলি একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলে, "ওঃ, হ্যাঁ, তাই তো। তুই তো সবে একটা উদাহরণ দিয়েছিস মাত্র। তার পশ্চাৎপট, পরিণতি কিছুই ব্যাখ্যা করিস নি। সরি, সরি, ভুল হয়ে গেছে।"সুমন বলে, "ঠিক আছে। ডোন্ট মাইন্ড। এই উদাহরণ বিশ্লেষণ করলে দেখবি এতে প্রকাশ পাবে কিছু পাশবিক প্রবৃত্তিগত আচরণ যা মানুষের মধ্যে আজও সুপ্ত ভাবে রয়ে গেছে। আবার দেখবি এমন কিছু প্রবণতা যা একান্তভাবে মানুষের মধ্যেই দেখা যায়। তা আবার পশুদের মধ্যে নেই। এই প্রবণতাগুলির কিছু ধনাত্মক - যা জ্ঞান, চেতনা, শুভবুদ্ধির উন্মেষের ফলে মানব চরিত্রে বিকশিত হয়েছে। কিছু প্রবণতা আবার ঋণাত্মক - যেগুলি মানুষের নিজের জীবনে বা সমাজে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। কখনো আপাতদৃষ্টিতে ঋণাত্মক বৈশিষ্ট্যর প্রভাবও হতে পারে সৃজনশীল। ফলে নানা পরিপ্রেক্ষিতে বিবিধ পরিণতি সৃষ্টিকারী প্রবণতাগুলি যথেষ্ট জটিল, কখনো বিতর্কিত। এগুলোকে এক ছাঁচে ফেলা খুব মুশকিল।ঈশু বলে, "এই মাত্র তুই যা বললি তা যেন loud thinking বা আত্মকথনের মতো লাগলো। মানে, তোর মনে কিছু ঘুরপাক খাচ্ছে যা তুই নিজের মনেই আওড়াচ্ছিস। একটু জটিল হয়ে যাচ্ছে জেঠু। একটু সহজ ভাবে বল না বাবা"।শিক্ষা দুর্নীতি রায় - একটি সারসংক্ষেপ - সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায় | মান্থা আবার ৫০ হাজার চাকরি খেয়ে নেবেন বলেছেন। তাই আগের রায়টা একটু কষ্ট করেই পড়ে ফেললাম। গ্রুপ-সি গ্রুপ-ডি, বাদ দিয়ে স্রেফ শিক্ষকদের নিয়েই লিখছি। কোন কোম্পানি স্ক্যান করেছে, সরকারের কী ভূমিকা, অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগ, এইগুলোও বাদ। এটা খুবই ছোট্টো সারসংক্ষেপ। বহু জিনিস বাদ যাবে। আমার বিচারে যেগুলো গুরুত্বপূর্ণ, সেগুলোই থাকছে। পুরোটা জানতে হলে অবশ্যই রায়টা পড়বেন, আমার মুখে ঝাল খাবেননা। মামলার গোড়া থেকে আমার করা সারসংক্ষেপ এরকমঃ ১। অযোগ্যদের সরানো নয়, পুরো প্যানেল যে বাতিল (সেট অ্যাসাইড) করতে হবে, এবং আবার অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিতে হবে, এই দাবীটা প্রাথমিক ভাবে তোলেন বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য। (পাতা ৯২-৯৩) ২। পিটিশনারদের আইনজীবী আশিষ কুমার চৌধুরি, এরকম কোনো দাবী তোলেননি, অন্তত তুলেছেন বলে লেখা নেই। চৌধুরি বলেন, যে, দুটো অনিয়ম হয়েছে। এক, পার্সোনালিটি টেস্টের নম্বর বাকি নম্বরের সঙ্গে যোগ করা হয়নি। দুই, সিনিয়ারিটি বিবেচনা করা হয়নি। এছাড়াও তিনি কিছু খুচরো অনিয়মের কথা বলেন। সবকটাতেই র্যাঙ্ক বদলে যায়, ফলে প্রকৃত যোগ্য চাকরি নাও পেতে পারেন, বা পিছিয়ে যেতে পারে। (পাতা ৯৪) ৩। এ পর্যন্ত ওএমআর শিটে কোনো অনিয়ম থাকতে পারে সেটা আসেনি। সেটা নজরে আনে সিবিআই। তারা এসএসসির ডেটাবেস সিজ করে। এবং গাজিয়াবাদ থেকে ওএমআর শিট স্ক্যান করেছিল যে কোম্পানি, তার কর্মচারী, জনৈক বনশালএর কাছ থেকে তিনটি হার্ডড্রাইভ উদ্ধার করে। সেই হার্ডড্রাইভ গুলোতে ওএমআর শিটের স্ক্যানড কপি ছিল। ওএমআর শিটের হার্ড কপি পাওয়া যায়নি, কারণ, এক বছর পরে সেগুলো আর রাখা হয়না। এই হার্ডড্রাইভের ওএমআর এবং এসএসসির তথ্যে কিছু গরমিল পাওয়া যায়। তারা এসএসসিকে দেয় মূল্যায়ন করে ব্যবস্থা নিতে। (এটা অনেকগুলো পাতার সারসংক্ষেপ, সংখ্যা দেওয়া মুশকিল।)৪। গাজিয়াবাদ থেকে উদ্ধার হওয়া হার্ড ড্রাইভ যে আসল না ওটা সিবিআই ম্যানিপুলেট করেছে, এই নিয়ে প্রচুর বাকবিতন্ডা চলে। ম্যানিপুলেট না করে থাকলেও ওটাই যে আসল, এবং সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণযোগ্য কিনা, এ নিয়েও চলে। কিন্তু এই আলোচনায় তাতে ঢোকা হবেনা। ৫। এসএসসি, তাদের তথ্য এবং গাজিয়াবাদের তথ্য খতিয়ে দেখে কোর্টকে রিপোর্ট দেয়, কতগুলোয় গরমিল আছে তা নিয়ে। একাধিক রিপোর্ট পেয়েছি রায়ে, কোর্ট শেষমেশ যেটা বলেছে, যে, বিশদ তুলনা করা হয়েছে (কারা কয়েছে লেখা নেই)। তার ফলাফল এরকমঃ শিক্ষক (ক্লাস সিক্স থেকে বারো) দের মধ্যে গরমিল আছে ১৮৫৯ জনের। (গ্রুপ-সি এবং গ্রুপ-ডিতে গরমিল আছে, ৫০০০+ ।) (পাতা ২৪০)৬। এসএসসির সার্ভারে তথ্য থাকলেও কোনো ওএমআর ইমেজ ছিলনা। তারা আরটিআই এর জন্য স্ক্যান কোম্পানির কাছ থেকে ইমেজ চেয়ে পাঠাত। তারা ওই ইমেজগুলোর সত্যতা মেনেও নেয়। সিবিআই এরও সেরকমই বক্তব্য। ( পাতা ২২৮) ৭। সব দেখে কোর্ট বলে, তার সামনে তিনটে জিনিস বেছে নেবার সুযোগ আছে। i) রিট পিটিশন বাতিল করা। ii) বেআইনী আর আইনী নিয়োগ আলাদা করে খুঁজে বার করা। iii) পুরো প্রক্রিয়াটাই বাতিল করা। ৮। কোর্ট তিন নম্বর জিনিসটাই বেছে নেয়। বেআইনী আর আইনী আলাদা করে খুঁজে বার করার চেষ্টা না করে। তার অনেকগুলো কারণ দেখায়। ক। যে কোম্পানিকে স্ক্যান করতে দেওয়া হয়, তারা সেটা সাবকন্ট্র্যাক্ট করেছিল। খ। এসএসসির সার্ভারে ওএমআর শিটের ইমেজ নাই। ইত্যাদি। যদিও সব পক্ষই একমত ছিল, যে, আসল ওএমআর শিট পাওয়া গেছে, এবং তা থেকে কোর্ট প্রতিটা গরমিল খুঁজেও বার করতে পেরেছে। সংখ্যাটা রায়েই আছে, আমিও ৫ নম্বর পয়েন্টেই লিখেছি। ফলে বেআইনী আর আইনী নিয়োগ বার করার কাজটা হয়েই গিয়েছিল, ধরে নেওয়া যায়। কিন্তু তারপরেও পুরো প্রক্রিয়াটাই বাতিল করা হয়। কারণ, পুরো মেশিনারিটাই এমন করে বানানো হয়েছে, যাতে করে দুর্নীতি "খুঁজে পাওয়া না যায়, পেলেও প্রমাণ করা না যায়"। সিবিআই দুর্নীতি হয়নি বলেনি। তারা খুঁজে বার করেছে। এসএসসিও দুর্নীতি অস্বীকার করেনি। কতটা হয়েছে তার পরিমাপও সিবিআই করে দিয়েছে। সেই অনুযায়ী শিক্ষকদের মধ্যে ২ হাজারের চাকরি যাবার কথা, বা সরকারের গাফিলতি প্রমাণ হবার কথা। সরকারের জন্য এটাই যথেষ্ট লজ্জার। কিন্তু তাতে তো যথেষ্ট শক তৈরি হবেনা। পুরো রায়টাই দাঁড়িয়ে আছে শক থেরাপি জাতীয় একটা ধারণার উপর। আমি তো আইনের ছাত্র নই, তবে স্বাভাবিক ন্যায়বিচার বলে একট প্রক্রিয়া আছে, আমরা জানি, যেখানে যা প্রমাণ হয়েছে, তার উপরে দাঁড়িয়েই বিচার হয়। যা খুজে পাওয়া যায়নি, প্রমাণ করা যায়নি, তার উপর দাঁড়িয়ে বিচার হয়, ক্রমশ জানছি। ২৬০০০ লোকের চাকরি খেয়ে তা নিয়ে উল্লাস করা যায় জানছি। এবং লোককে দিয়ে আট বছর খাটিয়ে মাইনে ফেরত চাওয়া যায় জানছি। এখন আইন-কানুন এই দিকেই চলেছে। মূল দাবীটা যার, সেই বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেছেন, কে যোগ্য কে অযোগ্য খুঁজে বার করা সম্ভব না। যারা টাকা দেননি, যোগ্য, তাঁদের আজকে সরকারকে প্রশ্ন করতে হবে, তোমরা দুর্নীতি কেন করেছিলে। এই প্রশ্নটা না করে তারা যদি প্রশ্ন করে, যে, সরকার দুর্নীতি করেছে বলে আমিই কেন শাস্তি পাব, সরকার দুর্নীতি করেছে বলে আপনার ওকালতি করার অধিকার কেড়ে নিলে কেমন হবে, তাহলে তিনি কি উত্তর দেন, জানার ইচ্ছে রইল। রায়ের লিংক - https://www.verdictum.in/pdf_upload/display-2024-04-22t130941416-1610751.pdfভোটুৎসবে ভাট - লক্ষ্মীবাবুর নকলি সোনার টিকলি - সমরেশ মুখার্জী | এখন বড় দুঃসময়। দূষণমুক্ত পরিবেশ, পর্যাপ্ত খাদ্য, পরিশ্রুত পানীয় এখন অধিকাংশ মানুষের ভাগ্যে নেই। ভাগ্যচক্রে আমি অতোটা দুর্ভাগা নই। তবে নিত্য নানান তিক্ত, খবর, পোষ্ট দেখে মন ভারাক্রান্ত হয়। অথচ কিছু করার নেই। কারণ SMW বা Social Media Warrior এর ভূমিকা ছেড়ে জমিতে 'কিছু' করার জন্য যে সব চারিত্রিক গুণাবলীর প্রয়োজন - সাহস, ক্ষমতা, উদ্যম, নিষ্ঠা, বিশ্বাস, সমর্পণ - সেসব কিছুই আমার চরিত্রে নেই। আমার সম্বল ভয়, সংশয়, আত্মকেন্দ্রিকতা। ফলে বাড়তে থাকে হতাশা, চাপ। চাপ কমাতে বই পড়ি। ভারী নয় - হালকা। টিভি দেখিনা বারো বছর। নেটে দেখি ডকু, ভ্রমণ ভিডিও। কিছুক্ষণ আত্মমগ্ন হয়ে থাকতে কিছু লিখি। বৃষ্টিভেজা পথকুকুরের মাথা ঝাঁকিয়ে জল ঝাড়ার মতো আমার লেখাও মনে জমা চাপ ঝাড়তে। তাতে ঋদ্ধ পাঠকের কাঙ্খিত সারবস্তু নেই। এসব নিছক আমোদিত কালক্ষেপ। Pleasurable Pastime. সুনীল বলেছিলেন, মাতৃভাষার চর্চায় মগজের পুষ্টি হয়। অসংলগ্ন ভাবনা গুছিয়ে ধরার প্রয়াস আমার কাছে cognitive exercise. তাই এসব লিখি। * * * * * * * * * * আটাত্তরের কাছাকাছি। নিউ এম্পায়ারে লবঙ্গলতিকার প্যাঁচের মতো তিনথাক গ্ৰীলের লাইনে ভ্যাপসা গরমে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে কাটতে হোতো ৭৫ পয়সার টিকিট। তারপর সিঁড়ি ভেঙ্গে পাঁচতলায় উঠে দূর থেকে কাঠের সীটে বসে সিনেমা দেখার মজা ছিল অনবদ্য। ওটা আদতে ছিল থিয়েটার হল - পি সি সরকার সিনিয়র ওখানে দেখিয়েছেন ম্যাজিক। তাই গদী আঁটা দামি টিকিটের আসন ছিল নীচে, মঞ্চের কাছে। সিনেমা হলে রূপান্তরিত হতে পাঁচতলার গ্যালারী হয়ে গেলো গরীব দর্শকের ৭৫ পয়সার স্বর্গ। ১৯৭৬ থেকে ৯০ - সেই স্বর্ণালী ১৪ বছরে ওখানে অনেক সিনেমা দেখেছি। এই প্রসঙ্গে আসছে একটা সিনেমার কথা - The Spaghetti Western Classic - The Good, The Bad and The Ugly. তখনকার হলিউডি ওয়েস্টার্ন সিনেমার পটভূমি ছিল পশ্চিম আমেরিকার টেক্সাস, আ্যারিজোনা, নেভাডা, উটা, কলোরেডো, নিউ মেক্সিকো, মন্টানা রাজ্যের দিগন্তবিস্তারি পাহাড়ি মরু অঞ্চল। ডাকাবুকো ডাকাত, ভাড়াটে খুনি, বাউন্টি হান্টার, জেল পালানো পলাতক - অর্থাৎ আইনকে কাঁচকলা দেখানো Outlaw বা দুর্বৃত্তরাই হোতো ঐ ধরনের সিনেমার প্রোটাগনিস্ট। রুক্ষ, শৈলকঠিন মুখ। পেটানো চেহারা। গায়ে বাঁটুল বা অরণ্যদেবের মতো সাত জন্মে না খোলা চামড়ার জ্যাকেট। মাইলের পর মাইল মরুপথে ঘোড়া ছুটছে ধূলো উড়িয়ে। যেন অতিপ্রাকৃত দৃশ্যপট। ধূ-ধূ প্রান্তরের মাঝে দ্বীপের মতো গুটিকয় ঘরের কোনো জনপদ। সেখানে এসে হাজির হয় আগন্তুক। সরাইখানার দরজায় ঝোলা ঘন্টি। ঢং আওয়াজ তুলে ঢুকলো ঘর্মাক্ত কলেবরে। তারপর ম্যাজিক - কাউন্টারে সরাই সেবিকা ভরা বসন্তের স্বর্ণকেশী। কাউন্টারে ঝুঁকে - she shows more than what she supposed to sell. মরুভূমিতে দৃশ্যমান মোলায়েম মরুদ্যান। মেদুর কটাক্ষে হেলায় তাকায় তারা আগন্তুক পানে। সেই কটাক্ষাঘাতে দূর্ধর্ষ দস্যুর দৃষ্টি হয়ে আসে মিয়োনো পাঁপড়ের মতো নরম। খেলা জমে ওঠার সম্ভাবনায় ৭৫ পয়সার টিকিটের ৫০ শতাংশ ওতেই উশুল। আইন শৃঙ্খলার বালাই নেই। পুলিশের টিকি দেখা যায় না। তাই আত্মরক্ষার্থে সবাই রাখে বন্দুক। দস্যুদের হাতে তা গ্যাস ওভেনে খটাস খটাস করে লম্বা পিজো-ইলেকট্রিক লাইটার জ্বালানোর মতো চলে অবলীলায়। পলক ফেলার আগেই ছোটে কয়েক রাউন্ড গুলি। সোয়াটার (flyswatter) ব্যাটের চপেটাঘাতে ফটাস ফটাস করে নিমেষে মরা মশার মতো হেথা হোথা ছিটকে পড়ে জলজ্যান্ত মানুষ। সেসব দৃশ্য বিস্মৃত জমানার। ফ্যাঁও ফ্যাঁও করে ম্যারিকান বুলিতে কী যে তারা বলতো তখন সিকিভাগও বুঝতাম না। এখন কষ্টেসৃষ্টে কিঞ্চিৎ বুঝি। তবু তখন কথা না বুঝেও দেখতাম। মজা লাগতো বেশ। হিরো, ভিলেন, সবার মাথায় ঝুলবারান্দার মতো কাউবয় হ্যাট। তার নীচে মরুভূমির উজ্জ্বল রোদে সরু চোখের দৃষ্টি। তাতে মেশা সাপের শীতলতা বা ঈগলের ক্রুরতা। নিভে যাওয়া চুরুট ভাবলেশহীন মুখে ওষ্ঠের কোনে অনর্থক চর্বিত হয়ে চলেছে। গলায় বাঁধা ব্যান্ডানা। কোমরে চামড়ার খাপে ঝিমোচ্ছে বিরাট নলের রিভলবার। দেখতে মোটেও শৌখিন নয় - তবে বহু ব্যবহারে চকচকে। হঠাৎ দেখে মনে হতে পারে বিহারী কুটিরশিল্প - মুঙ্গেরী 'কাট্টা' গোছের। কিন্তু না - হলিউড ওয়েস্টার্ন সিনেমায় দেখানো সে সব যন্ত্র এক একটি রত্ন বিশেষ। যেমন কোল্ট 1873 সিঙ্গল এ্যাকশন আর্মি স্পেশাল, .45 লং ব্যারেল কোল্ট, রেমিংটন 1858 নিউ আর্মি, কোল্ট প্যাটারসন, স্মিথ এ্যান্ড ওয়েসন শোফিল্ড ইত্যাদি। অর্ধশতাব্দীর অধিক প্রাচীন সেই সব মডেলের নির্ভরযোগ্যতা প্রশ্নাতীত। ঠিকমতো চালালে অব্যর্থ যমদূত। মানুষ তো ছার বেজায়গায় লাগলে ঘোড়াও জমি নিতে পারে। মজবুত কব্জি, হিমশীতল কলিজা না হলে কিলো খানেক ওজনের সেসব মারণাস্ত্র হঠাৎ খাপ থেকে তুলে চোখের পলকে চালানো সোজা কথা নয়। যেমন জন ওয়েন ঘোড়ার বসে একহাতে টুসকিতে ঘোরাতেন হেভি শটগান। দক্ষিণী রজনী অমন কায়দায় সিগারেট নিয়ে ঠোঁটে-আঙ্গুলে কেরামতি দেখাতেন। তাতেই উল্লসিত দেশী পাবলিক দিতো সিটি। অধূনা অনেকে দু আঙ্গুলে স্মার্টফোন ঘোরায়, তেমনই কায়দার ডিজিটাল ভার্সন বোধহয়। পুলিশ পিতার দৌলতে বছর আঠারো বয়সে একদা তাঁর স্মিথ এ্যান্ড ওয়েসন পুলিশ স্পেশাল সার্ভিস রিভলবারটি দেখার সুযোগ হয়েছিল। হয়তো সেটা ছিল .38 ক্যালিবারের মডেল 10 বা 15. কিন্তু কিলোখানেক ওজনের সেই লং ব্যারেল ধূসর যন্ত্রটির গাম্ভীর্যময় ধাতব শীতলতা ছিল বেশ সমীহ উদ্রেককারী। বলেছিলাম, একবার চালিয়ে দেখবো? বাবা বুলেট বার করে বললেন, চালা। তখন একটু ব্যায়াম ট্যায়াম করতাম, তাও একহাতে তুলে চালাতে কব্জি ও আঙুলে বেশ জোর লাগলো। বাবা বললেন, এটা এভাবে চালায় না, রিকয়েলের ঝটকায় কব্জিতে সটকা লাগতে পারে। এটা চালাতে হয় দুহাতে ধরে, এভাবে। এটা মেয়েদের হ্যান্ডব্যাগে রাখার উপযোগী পুঁচকে পিস্তল নয় যা স্বল্প দুরত্বে আত্মরক্ষায় চালাতে হতে পারে। এটা আরক্ষাকর্মীদের আইন শৃঙ্খলা রক্ষার্থে আক্রমণের উদ্দেশ্যে নির্মিত। তাই তাক করে চালাতে পারলে ৫০ ফুট দুরেও কোনো পলাতক দুর্বৃত্ত ধরাশায়ী হতে পারে। এখন নেট ঘেঁটে দেখলাম এর গুলি বেরোয় প্রায় ১০০০ ফুট/সেকেন্ড গতিতে। অর্থাৎ ৫০ ফুট দুরত্ব অতিক্রম করতে সময় নেবে ০.০৫ সেকেন্ড। মানুষের চোখের পলক ফেলার সময় ০.১০ সেকেন্ড। অর্থাৎ চোখের পাতা পড়ার অর্ধেক সময়ে ৫০ ফুট দুরে পলাতক ঘায়েল হবে। শুধু বুলেট গায়ে লাগা চাই। অভ্যাসের অভাবে পুলিশের গুলি এদেশে প্রায়শই লাগে ফুটপাতে হাঁটা বালকের গায়ে। ডাকাত পালায় পাঁচিল টপকে। তবে .38 পুলিশ স্পেশালের গুলি ৩০০ ফুট দুরত্বেও কারুর গায়ে লাগলে বেশ জখমের সম্ভাবনা। রাইফেলের গুলি পেড়ে ফেলতে পারে ১৬০০ ফুট দুরে কাউকে। টেলিস্কোপিক সাইট লাগানো হাই ক্যাপাসিটি স্নাইপার বা এ্যান্টি মেটেরিয়াল ব্যালাস্টিক রাইফেল তো ২কিমি দুরে কাউকে শুইয়ে দিতে পারে চিরনিদ্রায়। এখনো অবধি সর্বাধিক দূরত্বে ঘায়েল করার রেকর্ড ২.৪৭ কিমি। তার গুলি বেরোয় ৬৫০০ ফুট/সেকেন্ড গতিতে। দু কিমি দুরে কাউকে শোয়াতে সে বুলেট সময় নেবে মাত্র ১ সেকেন্ড। দুগ্গা দুগ্গা! প্রসঙ্গত বলি, এযাবৎ যাত্রীবাহী বিমানের সর্বাধিক গতির রেকর্ড আছে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের অধুনালুপ্ত সুপারসোনিক কনকর্ড বিমানের - ঘন্টায় ২১৮০ কিমি. এযাবৎ তৈরি সর্বোচ্চ ক্ষমতার স্নাইপার রাইফেলের বুলেটের গতিবেগ সে জায়গায় ঘন্টায় ৭১৫০ কিমি - কনকর্ড বিমানের ৩.৩ গুণ। একদা ওয়েস্টার্ন ছবিতে দাপিয়ে বেরিয়েছেন ক্লিন্ট ইস্টউড, জন ওয়েন, হেনরী ফন্ডা, ওমর শরীফ, বার্ট ল্যাঙ্কাস্টার, চার্লস ব্রনসন, টেরেন্স হিল, বাড স্পেন্সার, জেমস কোবার্ন, এলি ওয়ালচ্, লী ভ্যান ক্লীফ, বার্ট রেনল্ডস, রোনাল্ড রেগন (আমেরিকার চল্লিশতম রাষ্ট্রপতি হওয়ার আগে জীবনের শুরুয়াতি পর্বে) এবং কিয়দংশে গ্ৰেগরী পেক্, হামফ্রে বোগার্ট, ট্যালি স্যাভালস্, স্টিভ ম্যাকুইন, ইয়ুল ব্রেইনারের মতো অন্য গোত্রের অভিনেতারা। সে তুলনায় সেই সব ছবির অভিনেত্রীকুল - আমান্ডা ব্লেক, র্যাকোয়েল ওয়েল্চ, কেটি জুরাডো, রোন্ডা ফ্লেমিং, ডোনা রীড, ক্লেয়ার ট্রেভর - আপামর দর্শকদের স্মৃতিতে সেভাবে জায়গা করে নিতে পারেন নি। স্প্যাঘেটি ওয়েস্টার্ন সিনেমা বলতে বোঝাতো সেইসব ওয়েস্টার্ন ছবি যার মূল কলাকুশলীরা - প্রযোজক, পরিচালক, সম্পাদক, সঙ্গীতকার, ক্যামেরাম্যান হতেন ইতালিয়ান। যদিও বিশ্বের বাজারে বাণিজ্য করতে সেসব ছবির নায়ক নায়িকা হতেন মূলত হলিউডি। হলিউডে প্রতিষ্ঠিত ইতালিয়ান অভিনেতাও ছিলেন - টেরেন্স হিল, বাড স্পেন্সার, (Django খ্যাত) ফ্রাংকো নিরো ইত্যাদি। সে সব ছবি নির্মিত ও বিশ্ব বাজারে বিতরিত হোতো বিখ্যাত সব হলিউড প্রোডাকশন হাউস দ্বারা যেমন ওয়ার্নার ব্রাদার্স, এমজিএম, ইউনিভার্সাল পিকচার্স, কলম্বিয়া পিকচার্স, ইউনাইটেড আর্টিস্টস্ ইত্যাদি। এসব ছবি ইংরেজিতে হলেও ইতালিয়ান, স্প্যানিশ, জার্মান ভাষায় ডাবিং বা সাবটাইটেল দিয়ে তৈরী হোতো তার মাল্টিলিঙ্গুয়াল ভার্সন। The Good, The Bad and The Ugly নির্মিত হয়েছিল ১৯৬৬ সালে। পরিচালনায় ডিপ ক্লোজআপ ও লং ডিউরেশন শটের সাহায্যে সিচুয়েশন তৈরীতে সিদ্ধহস্ত বিখ্যাত ইতালিয়ান পরিচালক - সের্গিও লিওন। পদবীটা চেনা চেনা লাগছে? সানি লিওনের দৌলতে সেটা স্বাভাবিক তবে সের্গেইয়ের সাথে সানির কোনো যোগসূত্র নেই। সানি কানাডা প্রবাসী এক শিখ মেয়ে - করণজীৎ কৌর ভোরা। সানি তার ডাক নাম। ছোট থেকে খেলাধুলায় উৎসাহী, টমবয় স্বভাবের সানি রাস্তায় ছেলেদের সাথে হকি খেলতো। এগারো বছরে পেলো প্রথম চুম্বনের স্বাদ। ষোলো বছরে এক বাস্কেটবল খেলোয়াড়ের সৌজন্যে খেলাচ্ছলে হারালো কুমারীত্ব। একুশে পা দিয়ে ২০০১ সালের মার্চের পেন্টহাউস পত্রিকার প্রচ্ছদে নূন্যতম আচ্ছাদনে অপরিণত সম্পদে হাজির হয়েই পেলো 'পেন্টহাউস পেট' খেতাব। যেমন প্লেবয় ম্যাগাজিনে আবির্ভূতা মডেলরা পায় 'প্লেবয় প্লেমেট' তকমা। ২০০৭ সালে সানি বাণিজ্যিক প্রয়োজনে কৃত্রিম উপায়ে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ হোলো। যেমন অধূনা হোয়াটসএ্যাপ ফরোয়ার্ডেড পোষ্ট পড়ে (বা না পড়েই) সমৃদ্ধ হয় নেটিজেন। ২০১২তে পূজা ভাটের 'জিসম-2' দিয়ে বলিউডে হোলো সানির সাহসী আত্মপ্রকাশ। ভূতপূর্ব জীবিকা পরিত্যাগ করে প্রাচুর্যময় প্রতিস্থাপিত উপস্থিতিতে বলিউডে নিজেকে নবরূপে উদ্ভাসিত করায় সানির নিষ্ঠা ও শৈলী প্রশংসনীয়। সানির স্বামী ড্যানিয়েল ওয়েবারের সংস্কারহীনতা মধ্যবিত্ত মানসিকতায় অনুধাবনের অতীত। সানির লিওন পদবীটি দেন পেন্টহাউস পত্রিকার তদানীন্তন মালিক বব গুচ্চিয়ন। হয়তো তাঁর পদবীর শেষাংশের সাথে সমধ্বনীয় সাযুজ্যে - গুচ্চিয়ন - লিওন। এই আর কী। ইতালিয়ান পরিচালক সের্গেই লিওনের সাথে সানি লিওনের কেবল এটুকুই যোগসূত্র - এক পদবীতে। ফিরে আসি সের্গেইতে । তিনি বানিয়েছিলেন দুটি ট্রিলজি। প্রথমটি 'ডলার ট্রিলজি'। পরে 'ওয়ান্স আপন এ টাইম ট্রিলজি'। ডলার ট্রিলজির প্রথমটি ছিল A Fistful of Dollar (১৯৬৪)। দ্বিতীয়টি For a Few Dollars More (১৯৬৫) এবং শেষে ঐ TGTBATU (১৯৬৬). আগের দুটি ছবি তখন কেবল ইতালিতে মুক্তি পেয়েছে। দুটিতেই মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন ছ ফুট চার ইঞ্চির সুপুরুষ ম্যাচো ম্যান - ক্লিন্ট ইস্টউড। প্রথম ছবিটি আমেরিকায় মুক্তি পাবে ১৯৬৭তে। তবে তার আগেই সের্গিও বানাতে চাইলেন ট্রিলজির শেষ ছবি - TGTBATU. ছবির বাজেট মাত্র ১২ লক্ষ ডলার - বাস্তবিকই fistful - মুষ্টিমেয়। কিন্তু ততদিনে ক্লিন্ট বুঝে গেছেন নিজের বাজারদর। তাই চেয়ে বসলেন আড়াই লক্ষ ডলার - ছবির বাজেটের ২০% (আজকের দিনে ভারতীয় মূদ্রায় প্রায় ৫০ কোটি টাকা) এবং আমেরিকায় প্রদর্শনের লভ্যাংশের ১০%. কিঞ্চিৎ অসন্তুষ্ট হলেন সের্গেই। কিন্তু চাই তার ক্লিন্টকেই - কারণ The Good চরিত্র যা ভেবেছেন, তাতে তিনি নিশ্চিত - ক্লিন্ট মাত করবে বক্স অফিস। তাই রাজী হয়ে গেলেন। পরিচালকের মুন্সীয়ানা, চমৎকার ওয়াইড স্ক্রিন ক্যামেরার কাজ, সঙ্গীত পরিচালক এন্নিও মরিকনের অপূর্ব আবহ সঙ্গীত - পর্দায় ক্লিন্ট ও লী ভ্যান ক্লীফের চুম্বকীয় উপস্থিতি - সব মিলিয়ে এক ডেডলি প্যাকেজ। ক্লিন্টের এই ডলার ট্রিলজির সাফল্যই তাকে ১৯৭১ এ প্রতিষ্ঠিত করে আইকনিক 'ডার্টি হ্যারি' চরিত্রে। যার রেশ চলে ১৯৮৮ অবধি বিভিন্ন নামে মোট পাঁচটি ছবির সিরিজে। চতুর্থটির পরিচালকও ক্লিন্ট। ছবিতে তিনি সানফ্রানসিস্কো পুলিশ বিভাগের নির্ভীক এনকাউন্টার স্পেশালিস্ট - হ্যারি ক্যালাহান। মুম্বাই ক্রাইম ব্রাঞ্চের রিয়েল লাইফ এনকাউন্টার স্পেশালিস্ট দয়া নায়কের ওপরে তৈরি হয়েছিল 'অব তক ছপ্পন' সিনেমা। তাতে ইন্সপেক্টর সাধু আগাসের চরিত্রে ফাটিয়ে দিয়েছেন নানা। পরে ডলার ট্রিলজির প্রযোজকের বিনিয়োগও ফিরে এসেছে বহুগুণ হয়ে। সের্গেই বিখ্যাত হলেন Godfather of Spaghetti Western Movies হিসেবে। ১৮৬২ সালে আমেরিকান সিভিল ওয়ারের পটভূমিকায় তৈরি কাহিনী TGTBATU ছবির শেষে আছে একটি গোলাকার সমাধিক্ষেত্রের দৃশ্য - টানটান ক্ল্যাইম্যাক্সে ত্রিমূর্তীর মধ্যে সংঘটিত হবে ক্ল্যাসিক 'মেক্সিকান স্ট্যান্ডঅফ' দৃশ্য। তাতে আহবান জানায় ক্লিন্ট (Good)। ডাকুদের মধ্যে অলিখিত নিয়মে পুরুষোচিত অহংকারে তাতে সাড়া দিতেই হয় লী ভ্যান ক্লীফ (Bad) এবং নিরুপায় হয়ে এলি ওয়ালচ্কেও (Ugly). ক্ল্যাসিক ব্রিটিশ ডুয়েল হোতো দুজনের মধ্যে যাতে দুজন বা একজনের মরার সম্ভাবনা অবধারিত। মেক্সিকান স্ট্যান্ডঅফে সাধারণত তিনজন বন্দুকধারী নিজেদের মধ্যে হিসাব বরাবর করতে ১২০ ডিগ্ৰি কোনে দাঁড়িয়ে একে অপরকে মাপতে থাকে। যে আগে বন্দুক তুলবে সেই জ্বালবে স্ফুলিঙ্গ। ছবিতে Sad Hill Cemetery নামে পরিচিত ঐ সমাধিক্ষেত্রটি সেই ১৯৬৬ সালেই স্পেনের বুর্জোস প্রদেশে স্প্যানিশ সৈন্যদের দিয়ে পয়সার বিনিময়ে তৈরি হয়েছিল শুধুমাত্র ঐ একটি দৃশ্যের জন্য। দৃশ্যটি আমি বেশ কয়েকবার দেখেছি। এমন দীর্ঘায়িত নাটকীয় সাসপেন্স সৃষ্টিতে সের্গিও ছিলেন বিখ্যাত। সিনেমাটির দৈর্ঘ্যও তাই চার ঘন্টা। (দৃশ্যটার লিংক রইলো শেষে)। শুটিংয়ের পর ঝোপঝাড় কেটে বানানো নকল সমাধিক্ষেত্রটি পরিত্যক্ত হয়। ক্রমশ প্রকৃতি আবার অধিকার করে নেয় তাকে। তবে পৃথিবীব্যাপী TGTBATU ফ্যানদের স্বেচ্ছা দানে স্পেনের The Sad Hill Cultural Association ২০১৭ সালে - মানে দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর পর - বিস্মৃত, জঙ্গলাকীর্ণ সেই শ্যূটিং স্পটটি আবার খুঁজে বার করে। সাফ সাফাই করে সেটাকে রূপান্তরিত করে একটি নস্টালজিক পর্যটনস্থলে। পাঁচ দশক পরেও একটি পাতি এ্যাকশন সিনেমার প্রতি ফ্যানেদের এমন হৃদয়ের টান বেশ আশ্চর্যজনক। ১৯৭০ সালে শোলে ছবির কাহিনীকার সেলিম-জাভেদ যে তিনটি ছবি থেকে সবিশেষ প্রভাবিত হয়েছিলেন তার একটি ছিল সের্গেই লিওন পরিচালিত 'Once upon a time in the West' - মূখ্য ভূমিকায় হেনরি ফন্ডা ও চার্লস ব্রনসন। সে ছবির কাহিনী নির্মাণে সের্গেইয়ের সাথে যুক্ত ছিলেন আর এক দিকপাল ইতালিয়ান পরিচালক - বার্নার্দো বেত্রোলুচি। বাকি দুটি ছবি কুরোশোয়ার 'Seven Samurai' ও জন স্ট্রাজেসের 'The Magnificent Seven'. রাজ কুমার সন্তোষীর 'China Gate' ছবিতেও The Magnificent Seven এর সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। শোলের শ্যূটিংয়ের জন্যও ব্যাঙ্গালোর থেকে মাইশোরের পথে ৫০ কিমি দুরে রামনগরে হাইওয়ে থেকে ভেতরে ছবির প্রয়োজনে তৈরী হয়েছিল এক গ্ৰাম। প্রায় আড়াই বছর ধরে শ্যূটিং চলাকালে সেই অস্থায়ী গ্ৰামের নাম হয়ে গিয়েছিল 'সিপ্পি নগর'। স্থানীয় কিছু লোক কাজ পায়। তাদের দেখা গিয়েছিল সিনেমার পর্দায় গ্ৰামবাসী হিসেবে। ওখানেই জলের ট্যাঙ্কের ওপরে চড়ে ধর্মেন্দ্র করেছিলেন সেই বিখ্যাত সুইসাইড নাটক। কাছেই রামদেবরা টিলায় হয়েছিল গব্বরের ডেরা। সেখানে আমজাদ রাগে গরগর করতে করতে হুঙ্কার ছেড়েছিল - আরে, এ সাম্বা, কিতনা ইনাম রখ্খে হ্যায় রে সরকার হম পর? খাড়া গ্ৰানাইট পাথরের টঙে পা ঝুলিয়ে বসে সাম্বা বলেছিল - পুরা পচাশ হাজার, সরকার। এসব সংলাপ এখন কিম্বদন্তীপ্রায়। এখন সেই শোলে গাঁওয়ের কোনো অস্তিত্ব নেই সেখানে। সে জায়গা এখন বন্যপ্রাণ বিশেষজ্ঞদের কাছে অন্য কারণে গুরুত্বপূর্ণ। "রামদেবরা বেট্টা ভালচার স্যাংচুয়ারী" এখন বিলুপ্তপ্রায় ভারতীয় শকুনের সংরক্ষণের জন্য একমাত্র ঘোষিত ESZ (Notified Eco Sensitive Zone). অবশ্য ভারতের নানা জায়গা এখন ঘাস, ফুল, পদ্ম শোভিত এবং গদা, তরোয়াল, ত্রিশূল আন্দোলিত অন্য জাতীয় শকুনের মুক্তাঞ্চল - কেবল তাদের ডানা নেই বলে চট করে চেনা যায় না। তবে খুবলে নিলে টের পাওয়া যায়। তো যা বলছিলাম। সেই সমাধিক্ষেত্রের শেষ দৃশ্যে ক্লিন্ট ইস্টউড এলি ওয়ালচ্কে একটা বিলিয়ন ডলার ডায়লগ ঝাড়ে - “You see, in this world, there’s two kinds of people, my friend. Those with loaded guns and those who dig. You dig.” কিন্তু what to dig? সিনেমায় তা একটি বিশেষ কবরের নীচে লুক্কায়িত গুপ্তধন। বাস্তবে ক্ষমতাসীনদের শোষণে তাদের জন্য সম্পদ আহরণে নিম্নবর্গীয় মানুষের আমৃত্যু খুঁড়ে যাওয়া নিজেদের কবর। অথবা নির্মাণ করা নিজেদের জেল। যেমন আসামের দিনমজুর সরােজিনী হাজং। তিনি নিজেই নিজের জন্য বানাচ্ছেন জেল। সরােজিনীর মত অনেক দিনমজুর আসামে ডিটেনশন ক্যাম্প নির্মানে পেটের দায়ে ঘাম ঝড়াচ্ছেন, যাঁদের নাম আসামে চুড়ান্ত NRC তালিকা থেকে বাদ গেছে। তৈরী হলে ওখানেই স্থান হবে সরোজিনীদের। ১৯৭৩ সালে আমেরিকায় প্রতিষ্ঠিত হয় Grammy Hall of Fame. এখানে ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য প্রতি বছর কিছু বাছাই করা উচ্চমানের বা ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে এমন সঙ্গীত, বাদ্য, কন্ঠস্বর বা বক্তৃতা সংরক্ষণের জন্য মনোনীত হয়। তবে তা হতে হবে অন্ততপক্ষে ২৫ বছরের প্রাচীন - অর্থাৎ অবশ্যই থাকতে হবে তার enduring appeal. অনেক নমিনেশনের মধ্যে বিশেষজ্ঞদের ভোটাভুটির মাধ্যমে নির্বাচিত হয় অল্প কিছু। এভাবেই এখানে সংরক্ষিত হয়েছে টমাস আলভা এডিসনের ১৮৭৮ সালের রেকর্ডিং, ১৯৬৩ সালে মার্টিন লুথার কিং জুনিয়রের "I have a Dream" বক্তৃতা। বব ডিলান, বীটলস, এলভিস প্রেসলি, পল রবসন, বব মার্লে, ফ্রাংক সিনাত্রা, ইহুদি মেনুহিন, জন ডেনভার, এলটন জন, জন লেনন, সাইমন ও গারফাঙ্কেলের 'সাউন্ড অফ সাইলেন্স', বার্বারা স্ট্রেসান্ড্ ও এমন নানা দিকপাল গায়ক, বাদ্যকার, বাগ্মীর রেকর্ডিং। এখানে আছে ১৯৫৬ সালে হিচকক্ পরিচালিত - মুখ্য ভূমিকায় জেমস স্টূয়ার্ট ও ডোরিস ডে অভিনীত - The Man Who Knew Too Much সিনেমায় শেষ দৃশ্যে ডোরিসের স্বকণ্ঠে গাওয়া বিশ্ববিখ্যাত গান - Que Sera Sera - Whatever will be, will be গানটি, যার মর্মার্থ - বর্তমান পরিস্থিতিতে খুবই প্রযোজ্য - যা হবার, তাই হবে। (অহেতুক ভেবে কী হবে)। কিন্তু Grammy Hall of Fame এর অবতারণার কী হেতু? একটু খেয়াল করলে দেখা যাবে এই গরুর রচনায় - সানি লিওন থেকে গ্ৰ্যামী হল অফ ফেম - কোনো প্রসঙ্গই সম্পূর্ণ সম্পর্কবিযুক্ত নয়। প্রতিটি প্রসঙ্গের দড়িই কোনো না কোনোভাবে একটি মুখ্য গরুর গলায় বাঁধা - শেষবেষ ঘুরে ফিরে - 'সেই ঘাস গরু খায়' - করে প্রসঙ্গ আবার ফিরে আসবেই সেই গরুতে। এখানে সেই গরুটি TGTBATU. এ ছবিতে সের্গেইয়ের প্রতিটি ছবির সঙ্গীত পরিচালক এন্নিও মরিকনের একটি অনবদ্য থিম টিউন ছিল, যেটি পরে আইকনিক হয়ে যায়। সেটা আমি বহুবার শুনেছি - হয়তো অনেকেই শুনেছে। (তবু ড্যানিশ ফিলহারমনিক অর্কেস্ট্রা কর্তৃক সেটার রিক্রিয়েশনের ভিডিও লিংক রইলো শেষে। অবাক হয়ে গেছি দেখে - একটি সিনেমার টিউন তৈরিতে এতো হ্যান্ডস লাগে!) এন্নিও ছিলেন উঁচু দরের কম্পোজার। দীর্ঘ সঙ্গীতজীবনে তিনি ৭০টি পুরস্কারপ্রাপ্ত সিনেমায় ও টিভিতে প্রায় চারশোটি স্কোর ও একশোটি ক্ল্যাসিক সিম্ফনি কম্পোজ করেছেন। নিজে ছিলেন দক্ষ ট্রাম্পেট বাদক। TGTBATU সিনেমার সেই টিউনটি তাঁর পরিচালনায় পরিবেশন করে প্রাগ সিটি ফিলহারমোনিক অর্কেস্ট্রার শিল্পীবৃন্দ। এন্নিও পান ইতালির সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মান - OMRI (Order of the Merit of the Italian Republic) - যা আমাদের দেশের ভারতরত্ন সদৃশ। সঙ্গীতে নিবেদিতপ্রাণ মানুষটি ৬.৭.২০২০- পতনজনিত আঘাতে মারা যান ৯১ বছর বয়সে। তাঁর সুরকৃত TGTBATU সিনেমার সেই বিখ্যাত থিম টিউনটি গ্ৰ্যামী হল অফ ফেমের (GHF) অন্তর্ভুক্ত হয় ২০০৯ সালে। এবার হয়তো পাওয়া গেল GHF এর সাথে TGTBATU নিয়ে এই বাঁজা রচনার যোগসূত্র। এই বাঁজা রচনায় আমি খাল বিল থেকে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় আমার হালহীন মনপানসি ইচ্ছামতো ভাসিয়ে এমন ঘন্ট পাকিয়েছি যে মনযোগী পাঠকও হয়তো এযাবৎ পড়ে খেই হারিয়ে ভুলে যেতে পারে এ লেখার শিরোনামের তিলমাত্র তাৎপর্য তো এখনো অবধি বোঝা গেল না? চিন্তা নেই। এবার আসবে। সেদিন আবার শুনছিলাম ভি শান্তারাম প্রযোজিত ও পরিচালিত 'জল বিন মছলি নৃত্য বিন বিজলী' সিনেমায় মুকেশের কণ্ঠে আমার প্রিয় একটি গান - 'তারো মে সজকে'। বহুবার শুনেও সাধ না মেটা অনেক গানের একটি। ১৯৫৩ সালে সোহরাব মোদী প্রযোজিত, পরিচালিত 'ঝাঁসি কি রাণী' ছিল ভারতে নির্মিত প্রথম টেকনিকালার ছবি। ১৯৭১ সালে 'জবিম-নৃবিবি' সিনেমার প্রতিটি গান স্টিরিওফোনিক সাউন্ডে রেকর্ড করে শান্তারামও করূছিলেন আর এক রেকর্ড। রিমিক্সিং করেছিলেন মঙ্গেশ দেশাই, শান্তারামের রাজকমল কলামন্দির স্টুডিওতে। মজরুহ সুলতানপুরীর সরল সুন্দর কথা। লক্ষীকান্ত প্যারেলালের অনবদ্য সুর। সেই গানের শুরুতে (prelude) এবং মাঝে (interlude) TGTBATU সিনেমার সেই আইকনিক থিম টিউনটির সিগনেচার শিসটি এই গানে হুবহু ব্যবহৃত হয়েছে। তাই এই লেখার শিরোনাম 'লক্ষীবাবুর নকলি সোনার টিকলি'। চৌরঙ্গী, এলগিন, মুন্সীবাজার রোডে গেলে দেখা যাবে পর পর কয়েকটি 'লক্ষী বাবুকা আসলি সোনা চাঁদিকা দোকান'। সবকটিই প্রথম, একমাত্র এবং আসল। এই গানে ঐ শিস লক্ষ্মীদা জুটি প্যারসে নিজেদের বলে চালিয়ে দিয়েছেন নাকি ভদ্রতার খাতিরে এন্নিওর প্রতি অন্তত রোলিং ক্রেডিটে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছেন, জানা নেই। প্রতিমার মতো সুন্দর কপালে একটি ঝলমলে টিকলি ঝুললে ভালোই লাগে দেখতে। তবে তা না থাকলেও অসুন্দর লাগে না। 'তারো মে সাজকে' গানটিও তেমন। ঐ টিউনটি গানে অবশ্যই যোগ করেছে এক মনোহর মাত্রা। তবে তা না থাকলেও গানটি ভারতীয় আমেজের সুন্দর সুরের জন্য মোটেও খারাপ লাগতো না। মুকেশের গায়কীর গিটকিরি তো কান-মন জুড়ানো। লক্ষীকান্ত-প্যারেলাল জুটি সুরকৃত গানে ঐ টুকলি করা টিউনের টুকরোটাই এই গরুর রচনার প্রেরণা। তাই শিরোনামে জ্ঞাপন করেছি কৃতজ্ঞতা। তবে শেষ অবধি না পড়লে তা বোঝা সম্ভব নয়। এই টুকলির কথা জেনেছি তিন দশক আগে। দুঃসময়ে ছোট্ট স্ফূলিঙ্গ জোগায় অবান্তর রচনা লেখার প্রয়াসে আত্মমগ্নতায় ডুবে থাকার দাওয়াই। লেখার মশলা সংগ্ৰহকালে জানতে পারা যায় নানা আনন্দময় তথ্য। পলায়নবাদীরা এভাবেও এড়িয়ে থাকতে পারে বিষাক্ত বর্তমানের অভিঘাত।
জনতার খেরোর খাতা...
উনিশ নয় বিষ - Eman Bhasha | ১. মেক ইন ইন্ডিয়া ২. স্কিল ইন্ডিয়া৩. স্টার্ট আপ ইন্ডিয়া৪. স্মার্ট সিটি৪. দু কোটি করে বছরে চাকরি ৬. বিকাশ ৬. সুদিন ৭. আচ্ছে দিন ৮. গুজরাট মডেল ৯. উত্তমপ্রদেশ ১০. জিনিসপত্রের দাম কমানো ২৫%১১. ডলারের দাম কমিয়ে ৪০ টাকা১২. নোটবন্দি১৩. প্রতি ঘরে বিদ্যুৎ ১৪. জিএসটি ১৫. লক ডাউনের সুফল ১৬. থালা বাজানো১৭. ডিজেল পেট্রল কেরোসিন দাম কমানো১৮. সব লোকের মাথায় ছাদ ২০২২ মধ্যে১৯. প্রতি ক্ষেতে জলউনিশ বিষয়ে চুপ খালি বিশ নম্বর বিষয়ে বিশ ঢালা।বাকি নিয়ে কথা সব বন্ধ।১৯২৫ থেকে বলা -- হিন্দু মুসলমান হিন্দু মুসলমান আবার বলে চলেছে ফাটা রেকর্ডের মতোজালিয়াতিতে কোন রেয়াত নেই না ক্রিমিন্যাল কন্সপিরেসি। নাকি দুটোই !! - upal mukhopadhyay | ওএমআর শিটের গণ্ডগোলে সবাই ভুগলো কেন তার যুক্তি হিসেবে বিকাশ কোম্পানি 'জালিয়াতিতে কোন রেয়াত নেই' এই যুক্তিতে পুরো প্যানেলটা বাতিল করিয়েছে। এমনকি পার্থসারথী সেনগুপ্তের মতো উকিলকেও বলতে শুনলাম তিনি যুগপৎ আনন্দিত ও দুঃখিত । আনন্দের কারণ হল বিচার ব্যবস্থা কড়া হাতে' জালিয়াতিতে কোন রেয়াত নেই' এই অবস্থানে দৃঢ় থেকেছে। ওনার দুঃখের কারণ হল এতগুলো চাকরি যাওয়ায়। বিশেষত যখন এরা কেউ লাটসাহেবের বাড়ির ছেলেপিলে নয়। বিকাশ কোম্পানির কিন্তু কোন দুঃখ নেই। তাদের যুক্তি তৃণমূলকে ভোট দেবার সময় মনে ছিল না। পুরো বিজেপির ন্যারেটিভ খেয়ে বসে আছে জমিদারি হারানো ভদ্দরলোক সিপিএময়ের এই অংশটা। শুধু খেয়েছে নয় আগ্রাসী হয়ে লোক তাতাচ্ছে। এদের সংগঠন এবিটিএ, যারা স্টেক হোল্ডার, তাদের অবস্থান অবশ্য অন্য ট্রেড ইউনিয়নের মতোই কারণ তাদেরকেও এই রায়ের বিরুদ্ধে মামলা করতে ছুটতে হবে সুপ্রিম কোর্টে । সিপিএম রাজ্য কমিটির বয়ানেও এই বিকাশ কোম্পানির বিজেপি মার্কা উল্লাস নেই। 'জালিয়াতিতে রেয়াত নেই 'লজিকের বাইরে বিজেপির আর একটা এ্যাজেন্ডার দিকে কারু নজর পড়ে না। সেটা এই ফ্যাসিস্ট রায় দানকে প্রভাবিত করেছে লোক চক্ষুর আড়ালে। সেটা হল এই মামলায় পিএমএলএর প্রয়োগ । সারা ভারতের গণতান্ত্রিক মানুষ যার মধ্যে আইনজীবীদের বড় অংশ আছেন ,এই দানবীয় আইনের প্রয়োগের বিরোধী। যে কোন দুর্নীতির অভিযোগ উঠলেই সত্যাসত্য না দেখেই এর প্রয়োগ হচ্ছে।অবশ্য তৃণমূলের সরকারের পুকুর চুরি সুবিদিত ।আর এখানেই সব্বোনাশ হয়েছে , পি এম এল এ প্রয়োগ ঠিক মনে হচ্ছে ।কিন্তু একবার কোন মামলা প্রসঙ্গে এর প্রয়োগ হলে একটা ক্রিমিন্যল কন্সপিরেসির যুক্তি কোথাও না কোথাও মাথা চাড়া দেয় সে মামলার প্রতি পদক্ষেপে । অর্থাৎ 'জালিয়াতিতে রেয়াত নেই' বলে সবার চাকরি খাওয়ার রায়ের সময় শিক্ষকদের বিরুদ্ধেও ক্রিমিন্যল কন্সপিরেসির যুক্তিটা তলেতলে কাজ করে নাকি ? না হলে এতটা শ্রমিক কর্মচারী বিরোধী রায়দান হয় কি করে ?বিস্কুট, ড্রাগনের ধোঁয়া, মানভি এবং....... - Somnath mukhopadhyay | সমাজ মাধ্যমে একটি ভিডিও। সামাজিক মাধ্যমে ঠাঁই পাওয়া হালফিলের একটি পোস্ট। প্রেরক চিত্র পরিচালক মোহন জি। তাঁর পাঠানো ভিডিওটিতে দেখা যাচ্ছে, একটি ছোট বাচ্চা তার বাবার সঙ্গে রোবট মেলায় এসেছে জানতে, শিখতে,আনন্দ করতে। মেলা প্রাঙ্গণে জমজমাট ভিড়, বসেছে নানান লোভনীয় মুখে জল আনা সব খাবারের দোকান।সেখান থেকেই কিনেছে একটি ‘স্মোকি বিস্কুট’। পরমানন্দে তার মজায় মজেছে শিশুটি। ও মা! এ কি? বাচ্চাটি অমন কুঁকড়ে যাচ্ছে কেন? পেটে হাত দিয়ে মাটিতে শুয়ে কেন অমন ছটফটই বা করছে? ঐ বিস্কুট খেয়েই কি ওর এমনটা হলো? তাহলে ঐ বিস্কুটে কি এমন ছিল, যার ফলে শিশুটি এমন করছে? জানি, এইটুকু পড়েই আপনারা অনেকেই হয়তো প্রবলভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। আপনাদের এমনটা হওয়া স্বাভাবিক, খুব স্বাভাবিক। কেউ কেউ হয়তো ভাবছেন - আহা ! ঐ শিশুটির জায়গায় যদি আমার গোগোল, রেহান, তিন্নি কিংবা তূর্য থাকতো, তাহলে? এমন প্রতিক্রিয়া যে কোনো সংবেদনশীল মানুষের পক্ষেই খুব স্বতঃস্ফূর্ত, স্বাভাবিক। আপনাদের সকলের অবগতির জন্য, খুব মর্মাহত কন্ঠে জানাই ঐ শিশুটি, মেলা দেখতে আসা কর্ণাটকের শিশুটি …….. দুই রসায়নবিদ (!) ভাইয়ের কথা । কর্ণাটকের দেভাঙ্গারের মেলা প্রাঙ্গণ থেকে এবার চলুন সুদূর গাজিয়াবাদের নয়ডায়। এই শহরেই থাকে আমাদের চলতি কাহিনির দুই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র - বিশাল এবং বিকাশ । নামের এমন মিল দেখে নিশ্চয়ই ভাবছেন এরা দুইভাই নয়তো? ঠিকই ধরেছেন। আদিতে উত্তরপ্রদেশের মুজফ্ফর নগরের বাসিন্দা, তবে এখন ব্যবসার প্রয়োজনে দ্রুত জমজমাট হয়ে ওঠা নয়ডায় বসবাস করছে তারা। সোশ্যাল মিডিয়ায় এই দুই ভাই এবং তাদের আশ্চর্য আবিষ্কার ( ?! )এখন নাকি ভাইরাল। কী সেই আবিষ্কার, কীভাবেই বা তার উদ্ভাবন? এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার আগে আসুন এদের সম্পর্কে আরও কিছু কথা জেনে নেবার চেষ্টা করি।অন্য আর পাঁচ জনের মতো ছোটো বেলায় এই দুই ভাইকে ভর্তি করা হলো স্কুলে। কিন্তু স্কুলের পড়াশোনা আর নিয়মের কড়াকড়ি বিলকুল না পসন্দ ছিল এদের, বিশেষকরে বিশালের। পাঠ্য বিষয়গুলোর মধ্যে রসায়নের প্রতি তার একটা ভালোবাসা তৈরি হয়েছিল বটে কিন্তু পরীক্ষায় সেই ভালোলাগার বিষয়েও বিশাল অনুত্তীর্ণ হলো। রসায়ন ক্লাসে নতুন নতুন পরীক্ষার প্রতি তার এক মুগ্ধতার সম্পর্ক তৈরি হয়ে গিয়েছিল। একদিন রসায়নের ল্যাবক্লাসে ওদের রসায়নের শিক্ষক একটা চমৎকার পরীক্ষা করে দেখালেন। নাইট্রোজেন গ্যাসকে হিমায়িত করা হলে তা প্রথমে তরলে পরিণত হয় এবং খানিক সময় পরে তা ধোঁয়া হয়ে বেরিয়ে আসে। বা! এতো ভারি মজা! ছিল রুমাল হয়ে গেল বিড়াল গোছের আর কি !বিশাল অবাক হয়ে এই আশ্চর্য রূপান্তর প্রত্যক্ষ করল। সরস্বতীর আখড়ায় খুব বেশিদিন টিকে থাকা হয়নি তাদের, তবে ঐ পরীক্ষার বিস্ময়কর পরিণতির বিষয়টি তাদের স্মৃতিতে স্থায়ী আমানত হয়ে রয়ে গেল।স্কুল বেলার এই অভিজ্ঞতাকে পুঁজি করেই তারা তৈরি করেছে স্মোকি বা ধোঁয়া বিস্কুট। বিস্কুটের সঙ্গে মেশানো হয় নাইট্রোজেন। ফলে এই বিস্কুট খাওয়ার পর মুখ থেকে গলগলিয়ে বেরিয়ে আসে ধোঁয়া। পঞ্চাশ টাকা দরে এই বিস্কুট দূরদূরান্তের মেলায় ঘুরে ঘুরে বিক্রি করে তারা। মেলা প্রাঙ্গণে পৌঁছতে যেটুকু দেরি, বিস্কুট বিকিয়ে যেতে বিন্দুমাত্র সময় লাগেনা। ছেলে বুড়ো সবাই এই বিস্কুটের মজা নেয়। স্কুলজীবনের কাছে তাদের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। দিব্যি করে কম্মে খাচ্ছে তারা। মেলা ও ধোঁয়া বিস্কুট । ধোঁয়া বিস্কুট!! এমন কিসিমের বিস্কুট খাওয়া তো দূরের কথা অদ্যাবধি চোখেও দেখিনি। সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদনের সূত্র ধরে খোঁজ খবর নিতে গিয়ে যে তথ্য পেলাম তা রীতিমত উদ্বেগজনক। আমার চেনা পরিচিত পরিসরে এমন বিস্কুটের দেখা সেভাবে না পেলেও উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে এই বিস্কুটের প্রতি ক্রেতা সাধারণের আগ্রহ এবং আসক্তি দুইই দ্রুত হারে বেড়ে চলেছে। শপিংমল, বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত মেলা, সামাজিক বা পারিবারিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি অভিজাত রোস্তারা বা পথিপার্শ্বের হোটেল বা ধাবাতেও দেদার বিকোচ্ছে তথাকথিত ধোঁয়া বিস্কুট। তরল নাইট্রোজেনের রাসায়নিক ধর্মকে কাজে লাগিয়ে তৈরি হচ্ছে নানান ধরনের কুকিজ। বাতাসের সংস্পর্শে এলেই তা থেকে বের হয়ে আসছে ধোঁয়া, ক্রেতা - বিক্রেতা মহলে যা ‘ড্রাগনের শ্বাস’ নামে বহুল প্রচলিত। খাবারের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের মাইক্রোবস বা অণুজীবের সংক্রমণ ঠেকাতে তরল নাইট্রোজেনের ব্যবহারের চল বহুদিনের। তবে এই ব্যবহারের রীতি নিয়ম বিষয়ে সম্পূর্ণ অবহিত না হয়েই যদি কেউ যথেচ্ছভাবে এই তরলকে খাবারের আকর্ষণীয়তা বাড়িয়ে মুনাফা অর্জনের চেষ্টা করে তবে তা অত্যন্ত ঝুঁকির কাজ হবে। বড়সড় দুর্ঘটনার সম্ভাবনাকেও এড়িয়ে যাওয়া যায়না। কেন এমন আশঙ্কা করছেন সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীরা?প্রকৃতিগতভাবে তরল নাইট্রোজেন হলো এমন একটি তরল পদার্থ যার স্ফুটনাঙ্ক অত্যন্ত কম, -১৯৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস । এমন একটি তরল খাবারের মাধ্যমে শরীরে ঢুকলে তীব্র শ্বাসকষ্ট সহ শ্বাসনালীতে ছিদ্র সৃষ্টি হতে পারে। চামড়ায় লাগলে তা পুড়ে যেতে পারে। কর্ণাটক রাজ্যের বাচ্চাটির মতো আরও বহু মানুষ পৃথিবীর নানা প্রান্তে তরল নাইট্রোজেনের প্রভাবে আক্রান্ত হয়েছে । কারো গ্যাস্ট্রিক নালীতে ছিদ্র ধরা পড়ে, কারো আঙ্গুল বা হাতের তালু পুড়ে গিয়েছিল, কেউবা চরম শারীরিক অস্বস্তির কারণে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছে।এমন সমস্যা বা উপসর্গগুলোকে এড়িয়ে চলার জন্য তরল নাইট্রোজেন দিয়ে তৈরি খাদ্য বা তরল পানীয় গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। অবাঞ্ছিত পরিস্থিতিতে যাতে কেউ না পড়ে সেই জন্য FDA’ র তরফে কতগুলো সুপারিশ করা হয়েছে।১) খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুতিতে তরল নাইট্রোজেনের ব্যবহার এড়িয়ে যাওয়া সবথেকে নিরাপদ। একান্তই যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে ফুড গ্রেড নাইট্রোজেন ব্যবহার করতে হবে। ২) যে পাত্রে খাবারটি পরিবেশন করা হবে তাতে যেন তরল নাইট্রোজেন না থাকে। ৩) যে পাত্রে খাবার দেওয়া হবে সেই পাত্রের মুখটি অপেক্ষাকৃত ভাবে সরু হতে হবে যাতে একবারে অনেকটা খাবার হাতে তুলে নিতে না পারে গ্রাহক ভোক্তা। ৪) একবারে অনেকটা করে খাবার তুলে না নিয়ে একটা একটা করে মুখে পুরতে হবে। ৫) খাবারটি খাওয়ার সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া নিয়ে সুনির্দিষ্টভাবে বিধি সম্মত সতর্কতার কথা লেখা থাকতে হবে প্যাকেটের গায়ে। এতোসব বিধিনিয়মকে যথাযথ মান্যতা দিয়ে ধোঁয়া বিস্কুট বিক্রি করা হয় কিনা জানিনা, তবে একথা ঠিক শিশু কিশোর কিশোরী গ্রাহক মহলে ড্রাগন শ্বাস নামে পরিচিতি তরল নাইট্রোজেন যুক্ত ধোঁয়া বিস্কুট অত্যন্ত জনপ্রিয়। আমাদের ছেলে বেলায় আমরাও রঙিন ফাঁকি মিঠাই, টকটকে রঙের বরফ আইসক্রিম, ঝুরো বরফের ঠাণ্ডাই, চিনি আঁশিয়ে তৈরি রঙদার ফিতা মিঠাইয়ের প্রতি বেশ আসক্ত ছিলাম।ঐসব লোভনীয় বস্তুগুলো কতটা স্বাস্থ্যবিধি সম্মত উপায়ে তৈরি করা হতো সেই প্রশ্ন তখন সেভাবে ওঠেনি। এখন সময় বদলেছে, খানিকটা হলেও বেড়েছে উপভোক্তার সচেতনতা। ফলে আজকাল প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে এইসব লোভনীয় বস্তুর গুণমান নিয়ে। তবে ১৪০ কোটি মানুষের বাসভূমি আমাদের এই ভারতবর্ষের আনাচে কানাচে কখন কী কাণ্ড ঘটে চলেছে প্রতিনিয়ত তার খবর কে রাখে? তরল নাইট্রোজেন স্বাস্থ্যের পক্ষে মোটেই ভালো নয়। কেবল ধোঁয়া দেখিয়ে লোক টেনে, লাভের বহর বাড়ানোর এই ঝুঁকি বহল কারবার কবে বন্ধ হবে তাই এখন দেখার। অবশেষে স্বস্তি !! চিত্র পরিচালক মোহন জি সামাজিক মাধ্যমে যে ভিডিওটি প্রচার করেছিলেন তাতে বাবার সঙ্গে রোবট মেলা দেখতে আসা কন্নড় শিশুটি মারা গেছে বলে বলা হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে এমনটা হয়নি। এই খবর সকলের জন্যই পরম স্বস্তির ও আনন্দের। ছেলেটির বাবা জানিয়েছেন, যে ধোঁয়া বিস্কুট খাবার পর তার ছেলে গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি তখনই তাকে হাসপাতালে নিয়ে যান। ডাক্তারবাবুর চিকিৎসার কল্যাণে ছেলেটি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। অবশেষে স্বস্তি ফিরে এসেছে। **পুনশ্চ / মানভি আখ্যান কর্ণাটকের শিশুটির খবরে বেশ স্বস্তি নিয়ে রাত ভোজনের তোড়জোড় করতে না করতেই নজর পড়লো সেই খবর কাগজেই। স্কুল বেলার অভ্যাস, তাকে এখনও ছাড়তে পারিনি। এবারও চোখে ধরা পড়েছে একটি করুণ পরিণতির কাহিনি। অকুস্থল পাঞ্জাবের পাতিয়ালা শহর। ছোট্ট মেয়ে মানভি। গত ২৪ মার্চ ২০২৪, ছিল তাঁর দশম জন্মদিন। এমন খুশির দিনে বাড়িতে আয়োজন করা হয় এক সান্ধ্য অনুষ্ঠানের। বাড়ির একান্ত পরিজনদের পাশাপাশি সেখানে হাজির হয়েছিল মানভির স্কুলের কয়েকজন বন্ধু আর তাদের মায়েরা। সময় একটু একটু করে কেটে যায় খুশি আর মজায় মাখামাখি হয়ে । আসে সেই আকাঙ্খিত মুহূর্ত – কেক কাটার মহালগন। পাতিয়ালা শহর থেকে অনলাইনে অর্ডার দিয়ে আনা হয়েছে এক পেল্লায় সাইজের চকোলেট কেক - জন্মদিনের শুভেচ্ছা স্মারক। মানভি তার হাতে ধরা ছুড়ি দিয়ে কেকটাকে কাটে, কেকের চারদিকে সাজিয়ে রাখা মোমবাতিগুলো ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দেয়, চারপাশে ভিড় করে থাকা অতিথি অভ্যাগতরা হাততালি দিতে দিতে গলা চড়িয়ে গান গেয়ে ওঠে – Happy Birthday to You, Happy Birthday to You. Happy Birthday to You Manvi, Happy Birthday to You. এর পরের অংশটা সত্যিই মর্মান্তিক। কেকের প্রথম টুকরোটা নিজের মুখে পোরে মানভি, আর তারপরেই বমি করতে থাকে সে। অত্যধিক গরমে এমনটা হয়েছে মনে করে বাড়িতেই তার প্রাথমিক শুশ্রূষা চলতে থাকে। তবে মানভির শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। তাকে সুস্থ করে তুলতে দেওয়া হয় অক্সিজেন। কিন্তু চিকিৎসকদের সমস্ত চেষ্টাকে বিফল করে ছোট্ট মেয়ে মানভি মারা যায়। কেন এমন পরিণতি হলো ছোট্ট মেয়েটির। জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক ড: বিজয় জিন্দালের মতে, কেকের মিষ্টতা বাড়াতে আজকাল অত্যধিক মাত্রায় সিন্থেটিক সুইটনার ব্যবহার করা হয় যা স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক। কৃত্রিম উপায়ে তৈরি এই শর্করা খুব দ্রুত রক্তের শর্করার মাত্রা বাড়িয়ে দেয় যা প্রাণঘাতী হয়ে ওঠে। মানভির ক্ষেত্রে হয়তো এমনটাই হয়েছে । নাহলে বয়স নিরপেক্ষ ভাবে সকলের কাছে জনপ্রিয় কেকের মতো একটি খাবার এমন বিপদ ঘটাবে কেন?আমাদের অবহেলায় মানভির মতো ফুলেরা অসময়ে শুকিয়ে যায়। আমাদের চেতনা কি তাতে জাগে?? * তথ্য সূত্র এই নিবন্ধটি লেখার জন্য বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। এজন্য আমি সকলের কাছে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। মানভির পরিবারের প্রতি রইলো গভীর সমবেদনা।*অজ্ঞাত কারণে এই নিবন্ধের সঙ্গে প্রয়োজনীয় ছবিগুলো যোগ করা গেলনা। এ জন্য দুঃখিত।
ভাট...
 &/ | এমনও হতে পারে ২৬ হাজারের দেওয়া ঘুষের প্যাকেট আছে। অর্থাৎ পরীক্ষার ফলাফলে ঘাপলা অথবা ঘাপলা নয়, সব ক্ষেত্রেই 'পারিতোষিক' দিয়ে চাকরি পেতে হয়েছে। সেক্ষেত্রে ঘুষ যারা নিয়েছে তাদের শাস্তির দাবী ওঠা সবচেয়ে আগে দরকার।
&/ | এমনও হতে পারে ২৬ হাজারের দেওয়া ঘুষের প্যাকেট আছে। অর্থাৎ পরীক্ষার ফলাফলে ঘাপলা অথবা ঘাপলা নয়, সব ক্ষেত্রেই 'পারিতোষিক' দিয়ে চাকরি পেতে হয়েছে। সেক্ষেত্রে ঘুষ যারা নিয়েছে তাদের শাস্তির দাবী ওঠা সবচেয়ে আগে দরকার। aranya | সরি, দ। বক্তব্য মনে আছে, কিন্তু বক্তাদের নাম কিছুতেই মনে পড়ছে না। স্মৃতির অবোস্তা খুবি খ্রাপ :-(
aranya | সরি, দ। বক্তব্য মনে আছে, কিন্তু বক্তাদের নাম কিছুতেই মনে পড়ছে না। স্মৃতির অবোস্তা খুবি খ্রাপ :-( lcm | ওহ! মাইনে ফেরত সকলের জন্য নয়। আচ্ছা। কিন্তু তাহলে, চাকরি খোয়ানো ২৬০০০ এর জন্য কেন, সেটাও তো শুধু যাদের গোলমালের প্রমাণ আছে তাদের জন্য হওয়া উচিত। কনফিউজিং !
lcm | ওহ! মাইনে ফেরত সকলের জন্য নয়। আচ্ছা। কিন্তু তাহলে, চাকরি খোয়ানো ২৬০০০ এর জন্য কেন, সেটাও তো শুধু যাদের গোলমালের প্রমাণ আছে তাদের জন্য হওয়া উচিত। কনফিউজিং !
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাসিএএ-র ফাঁদে মতুয়ারা - শান্তনীল রায়
২৫ এপ্রিল ২০২৪ | ৬১ বার পঠিতবাংলার উদ্বাস্তু প্রধান এলাকাগুলিতে কান পাতলেই শোনা যায় নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে নানা গুঞ্জন। চব্বিশের লোকসভা ভোটে এই অঞ্চলগুলিতে জিততে বিজেপির মাস্টার্স স্ট্রোক এই নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ)। বিজেপি বারবার করে বলছে, সিএএ নাগরিকত্ব প্রদানের আইন, নাগরিকত্ব হরণের নয়। আর সেই আশাতেই বুক বেঁধেছে এক বিরাট সংখ্যক উদ্বাস্তু মানুষ। সিএএ-র বিষয়ে সম্যক ধারণা ছাড়াই। তবে দেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত সাহ দেশবাসীকে যেভাবে ক্রোনোলজি বুঝিয়েছিলেন, তা থেকে অতি সহজেই অনুমান করা যায় যে বিজেপির মনোবাসনা কেবল সিএএ -তে থেমে থাকবার নয়। প্রথমে সিএএ, তারপর এনআরসি (জাতীয় নাগরিক পঞ্জী)। আর যার পরিণতি হতে পারে উদ্বাস্তুদের জন্য ভয়ানক।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালদোলজ্যোৎস্নায় শুশুনিয়ায় - ৬ - সমরেশ মুখার্জী
২৫ এপ্রিল ২০২৪ | ৪৩ বার পঠিতআশির দশকে যাদবপুরের কয়েকটি ছাত্রছাত্রী শুশুনিয়া পাহাড়ে গেছে শৈলারোহণ অভ্যাস করতে - সেই ভিত্তিতে এই আখ্যান … এখন জোৎস্না উজ্জ্বল। তিনজন গভীর অভিনিবেশে তাকিয়ে আছে সুমনের দিকে। সুমন বলে চলে, "আদিমানবের আদিতেও ছিল কয়েক কোটি বছরের ক্রমবিবর্তনের ধারা। ফলে পশুসমাজের নানান প্রবৃত্তিগত বৈশিষ্ট্য আদিমানবের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছিল। বহু কোটি বছরের সঞ্চিত প্রবৃত্তিগত বৈশিষ্ট্য বা instictive characteristics মাত্র এক কোটি বছরের বিবর্তনের ফলে বিশেষ পরিবর্তিত হওয়া সম্ভব নয়। ফলে পশুসূলভ নানা প্রবৃত্তিগত বৈশিষ্ট্য বিবর্তিত মানুষের মধ্যেও সুপ্ত ভাবে রয়ে গেল..
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাবিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে…….. - সোমনাথ গুহ
২৫ এপ্রিল ২০২৪ | ৯৯ বার পঠিতমার্চ ও এপ্রিল পরপর দু মাসে দুজন স্বনামধন্য সমাজ ও মানবাধিকার কর্মী দীর্ঘ কারাবাসের নরক-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়েছেন। গত ৭ই মার্চ অধ্যাপক জি এন সাইবাবা প্রায় এক দশকের কারাবাসের পর নাগপুর সেন্ট্রাল জেল থেকে মুক্তি পান। এর প্রায় এক মাস বাদে ভীমা কোরেগাঁও (বিকে) মামলায় ধৃত নারী ও দলিত অধিকার কর্মী, অধ্যাপক সোমা সেন জামিন পান। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর এই দুজনের মুক্তি অবশ্যই স্বস্তিদায়ক, কিন্তু যা ঢের বেশি অস্বস্তিকর তা হচ্ছে তাঁদের গ্রেপ্তার, তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাঁদের বিচার বা বিচার না-হওয়া পুরো বিচারব্যবস্থার স্বরূপকে নগ্ন করে দিয়েছে। সাইবাবার কাহিনি বহু চর্চিত, তবুও সেটাকে আমরা ফিরে দেখব এবং কোন কারণে অধ্যাপক সোমা সেন সহ ভীমা কোরেগাঁও মামলায় ধৃত অন্যান্যদের এতো বছর কারাবাস করতে হল, এবং কয়েকজনকে এখনো করতে হচ্ছে, সেটা বোঝার চেষ্টা করব।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালশিক্ষা দুর্নীতি রায় - একটি সারসংক্ষেপ - সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায়
২৫ এপ্রিল ২০২৪ | ৩২৫ বার পঠিতমামলার গোড়া থেকে আমার করা সারসংক্ষেপ এরকমঃ ১। অযোগ্যদের সরানো নয়, পুরো প্যানেল যে বাতিল (সেট অ্যাসাইড) করতে হবে, এবং আবার অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিতে হবে, এই দাবীটা প্রাথমিক ভাবে তোলেন বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য। ২। পিটিশনারদের আইনজীবী আশিষ কুমার চৌধুরি, এরকম কোনো দাবী তোলেননি, অন্তত তুলেছেন বলে লেখা নেই। চৌধুরি বলেন, যে, দুটো অনিয়ম হয়েছে। এক, পার্সোনালিটি টেস্টের নম্বর বাকি নম্বরের সঙ্গে যোগ করা হয়নি। দুই, সিনিয়ারিটি বিবেচনা করা হয়নি। এছাড়াও তিনি কিছু খুচরো অনিয়মের কথা বলেন। সবকটাতেই র্যাঙ্ক বদলে যায়, ফলে প্রকৃত যোগ্য চাকরি নাও পেতে পারেন, বা পিছিয়ে যেতে পারে।
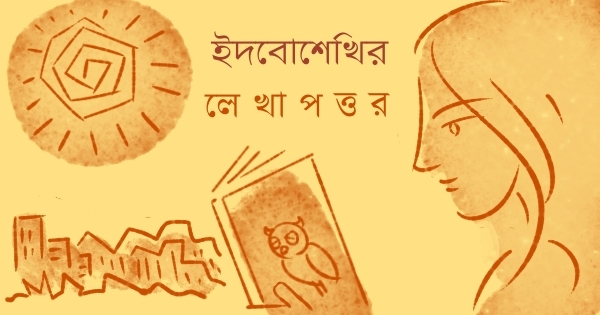 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাইদবোশেখির লেখাপত্তর - গুরুচণ্ডা৯
২৪ এপ্রিল ২০২৪ | ১০৯৩ বার পঠিতআমরা আপনাদের কাছে ডাক পাঠিয়েছিলাম তাদের খপ করে ধরে ফেলে, ঝপ করে লিখে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিতে। এসে গেছে তারা। আগামী কয়েকদিন ধরে রোজ দুটি-তিনটি করে তারা এসে হাজির হবে বুলবুলভাজার পাতায় - টাটকা ভাজা, গরমাগরম। পড়তে থাকুন। ভাল লাগলে বা না লাগলে দুই বা আরো অনেক লাইন মন্তব্য লিখে জানিয়ে দিন সে কথা। মন চাইলে, গ্রাহক হয়ে যান লেখকের।
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাউনিশে এপ্রিল - সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায়
২৪ এপ্রিল ২০২৪ | ১৮৭ বার পঠিতমীরজাফর তো শুনে হাঁ। কুচ মানে? এ কি রাজকার্য না ফুক্কুড়ি, যে সক্কালবেলা একটু মেজাজ খারাপ হয়েছে বলে লালমুখোদের সঙ্গে একদম যুদ্ধে নেমে পড়তে হবে? রাজা-বাদশাদের খেয়ালকে একটু তোয়াজ করতে হয়—সবাই জানে, কিন্তু এই আস্ত গাছপাঁঠাটা যেমন আহাম্মক, তেমনই বদমেজাজি—রাজনীতি তো বোঝেই না, আদবকায়দাও না। নবাব না হনুমান বোঝা মুশকিল, ওদিকে ধড়িবাজি আছে দুশো আনা। কোন এক ভাগাড় থেকে তুলে এনে মোহনলালকে মহারাজা বানিয়ে মাথার উপর বসিয়েছে, সেটা আবার ওর চেয়েও এককাঠি বাড়া। সে মালটা বিষ খেয়ে অবশ্য এখন আধমরা, দরবারে নেই—এই এক রক্ষে।
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাকবিতাগুচ্ছ - বেবী সাউ
২৪ এপ্রিল ২০২৪ | ১৫৯ বার পঠিতমানুষকে কখনো কখনো শার্দূল হয়ে উঠতে হয় / বাড়িতে তখন পোষ মানানো হচ্ছে / কুকুরের বাচ্চা / পোষ্য এবং পোষক দু'জনেই লোভনীয় / খোঁড়া পা নিয়ে আমার বিপ্লবী জেঠু / শার্দূলকে ভেবে বসছে কুকুর / কুকুর নিজেকে জেঠু ভেবে / সেজে উঠছে অযোধ্যায় যাবে বলে / পোষ্যদের খাদ্য প্রয়োজন / প্রয়োজন সঠিক সময়ে / সঠিক সমস্যা বোঝা / একটা হাড়ের লোভে শার্দূল ছুটছে / পেছনে পা খুঁড়িয়ে জেঠু / হাড় এবং / লোভ এবং / খোঁড়া পা / হো হো করে হেসে উঠছেন / আমাদের প্রণম্য / সন্তোষ রাণা
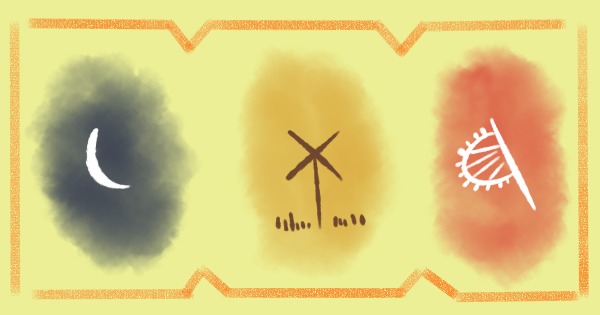 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাইদ বৈশাখ মানে মা - ইমানুল হক
২৪ এপ্রিল ২০২৪ | ৭৭ বার পঠিতসকাল সকাল একটা আম পাই। তার গায়ে সদ্য পাড়া আঠার গন্ধ। যাঁরা এই গন্ধ জানেন, তাঁরা মানবেন, কীভাবে মাতাল করে তোলে এই গন্ধ। কোনও কৃত্রিম গন্ধ একে প্রতিস্থাপন করতে এখনও পারে নি। অন্তত আমার জানা মতে। সোঁদা মাটির গন্ধ একেক জায়গায় একেক রকম। একেকটা আমের জাতের একেক রকম গন্ধ। কিন্তু আঠার গন্ধ বোধহয় এক। নাহলে ৬-১০ বছরের এক বালকের নাকে স্মৃতিতে ডুব মেরে থাকা গন্ধ কীভাবে আজ ঝড় তুলে দিলে প্রৌঢ় মনে! মায়ের গায়ের গন্ধ যেমন শিশুকে চিনতে শেখায়, তেমন আমের গন্ধ সাবালকত্বকে। একা একা আম পাড়া ঢিল মেরে, গুলতি ছুঁড়ে, আঁকশি দিয়ে, আরেকটু বড় হলে গাছে উঠে--সাবালকত্বের লক্ষণ। বয়স নয়, আনন্দের। পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়া যেমন আরেক আনন্দ। আনন্দের কী কোনও ব্যাঙ্ক আছে? এআই কী এই আনন্দ কোনও দিন দিতে পারবে? পারবে লিখতে সহজ সহজ সুখ আর অতি সরল আনন্দের গন্ধের কথা। মায়ের হলুদ মাখা আঁচলের, গায়ের গন্ধ কি দিতে পারবে কোনও রোবট?
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাবুড়োশিবতলা - পায়েল চট্টোপাধ্যায়
২৪ এপ্রিল ২০২৪ | ১৭৩ বার পঠিতজলের মধ্যে গোলা নীল রংটা নিজের গালে ঘষছে সুদাম।ঘষতে ঘষতে একটা মুখ মনে পড়ছে। সিনেমার মত। তারপর হঠাৎ নিজের আয়না দেখা মুখটা মনে পড়েছে। শুষ্ক, খড়খড়ে। একটা যন্ত্রণা ঠেলে উঠে আসছে। রংটা জোরেই ঘষে দিচ্ছে ও। হঠাৎ ব্যথায় কঁকিয়ে ওঠে। ওঠারই কথা। তবে গালের ব্যথায় নয়, মনের ব্যথায়। গৌরী যদিও ইচ্ছে করে মারেনি। সুদাম এক বুক কাদার মধ্যে একেবারে পা ডুবিয়ে সিনেমার হিরোদের কায়দায় গৌরীকে কথাটা বলতে চেয়েছিল। "এখুনি আন্ধার নামবে, তুই পাড়ার ওই ম্যাদামারা ছেলেটা না! কথা বলার মুরোদ নেই, এমন গায়ের কাছে এসেছিস কেন? দেখছিস লা কাজ করতিছি ক্ষেতে! যা এখান থেকে!" কথাগুলো বলেই কোদালটা হাতে তুলে নিয়েছিল গৌরী। কাজ করার জন্যে। সুদাম এত কাছে এসে পড়েছিল যে কোদালের বাঁটের আঘাত লাগতে একটুও দেরী হয়নি।
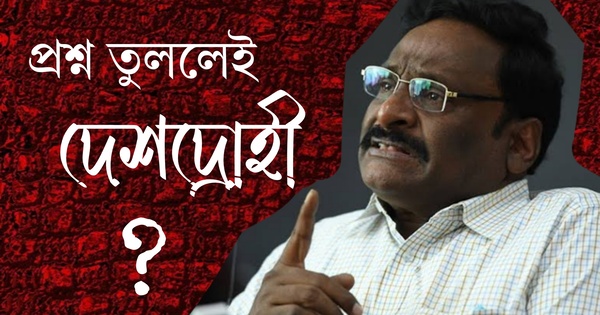 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাশাসককে প্রশ্ন করলেই দেশদ্রোহিতার তকমা! - ডঃ দেবর্ষি ভট্টাচার্য
২৩ এপ্রিল ২০২৪ | ২২৮ বার পঠিতগোকারাকণ্ডা নাগা (জি এন) সাঁইবাবা। পোলিও রোগে আক্রান্ত হয়ে শৈশবকাল থেকেই শারীরিকভাবে পঙ্গু। ফলস্বরূপ, পাঁচ বছর বয়স থেকেই হুইল চেয়ার ছাড়া চলাচলে অক্ষম। মানুষের অধিকার রক্ষার আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী। বিদগ্ধ লেখক। রাষ্ট্রীয় দমন পীড়নের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদী। রাষ্ট্রীয় মদতে সংগঠিত ‘অপারেশন গ্রীনহান্টের’ কট্টর সমালোচক। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ রামলাল আনন্দ কলেজের ইংরাজি বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক। বর্তমান বয়স ৫৭ বছর। শারীরিকভাবে ৯০ শতাংশ প্রতিবন্ধী এবং প্রায় চলৎশক্তি রহিত। আত্মগোপন করে থাকা মাওবাদীদের লেখাপড়া শিখিয়ে রাষ্ট্র বিরোধী হিংসাত্মক কার্যকলাপে প্ররোচিত করার অভিযোগে ২০১৪ সালের ৯ই মে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালভোটুৎসবে ভাট - লক্ষ্মীবাবুর নকলি সোনার টিকলি - সমরেশ মুখার্জী
২৩ এপ্রিল ২০২৪ | ৩৩৩ বার পঠিতদুঃসময়ে ছোট্ট স্ফূলিঙ্গও জোগায় অবান্তর রচনা লেখার প্রয়াসে আত্মমগ্নতায় ডুবে থাকার দাওয়াই। লেখার উপাদান সংগ্ৰহকালে জানা যায় নানা চমকপ্রদ বা আনন্দময় তথ্য। পলায়নবাদীরা এভাবে এড়িয়ে থাকতে চায় বিষাক্ত বর্তমানের অভিঘাত।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালচান রাত! - মহম্মদ সাদেকুজ্জামান শরিফ
২৩ এপ্রিল ২০২৪ | ৩৩১ বার পঠিতযাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আছে তাঁদের আমাদের মতো এমন সৌখিন চিন্তা ভাবনা করার ফুসরত নাই। শেষ মুহূর্তে কেনাকাটার হিড়িক লাগে কেন জানি। কিছু মানুষই আছে যারা কোন অজ্ঞাত কারণে সারা মাস কেনাকাটার আশপাশ দিয়েও যেতে রাজি না। প্রথম থেকেই নিয়ত পাকা যে তিনি যাবেন চান রাতেই! কেউ কেউ তো এমনও বলে যে চান রাত ছাড়া শপিং করে মজাই পাওয়া যায় না। কেউ চান রাত ছাড়া আবার ইদ শপিং হয় না কি? এমন প্রশ্নও করে। তো এই খদ্দেরদের জন্য চান রাতে চলে ভোর পর্যন্ত জমজমাট কেনাকাটা। রাত একটা দুইটা তিনটা যেন সন্ধ্যা রাত! ঢাকায় কোন দিন ইদ করা হয়নি। কিন্তু বন্ধুদের অনেকের কাছেই শুনেছি যে ঢাকায় চান রাতের জৌলুসের সাথে কোন কিছুর তুলনাই হয় না। দেড় দুই কোটি মানুষ চান রাতের আগে ঢাকা ছেড়ে চলে গেছে। ঢাকা হাঁফ ছেড়ে গা ঝাড়া দিয়ে দাঁড়িয়েছে। যারা বের হচ্ছে তারা চলে ফিরে, দেখে শুনে, কিনে না কিনে আলাদা সুখ পাচ্ছে। ঢাকার জ্যাম ঘাম গরম যে দেখছে সে চান রাতে না থাকলেও অনুমান করতে পারে যে কতটা হালকা লাগছে সবার এই দিন!
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাসুর - অনুরাধা কুন্ডা
২৩ এপ্রিল ২০২৪ | ২৯৮ বার পঠিতফোন বেজে উঠতেই শ্যামশ্রীর গলা ভেসে এলো। ছটফটে, তরতরে শ্যামশ্রীর গলা নয়। রাগী, কড়া শ্যামশ্রীর গলাও নয়। চটপটে, স্মার্ট নয়। একটু ভেজা ভেজা। দরদী। নরম। ত্রিলোকেশের এখন ঠিক যেমন দরকার তেমনটি। যখন যেমন দরকার, তেমনটি। যখন খোলামেলা চাই তখন খোলামেলা। যখন লাজুক চাই তখন লাজুক। যখন লাস্য চাই তখন লাস্য। এইভাবেই। ঠিক এইভাবেই প্রোগ্রামড করা আছে। কন্ঠস্বর, চলাফেরা, ওঠাবসা, ফুড হ্যাবিট, যৌনতা , এমনকি পটি টাইমিং পর্যন্ত। শ্যামশ্রী না। শ্যামশ্রীর ক্লোন। শ্যামশ্রী দত্তগুপ্ত টু। হাইট পাঁচ পাঁচ। রঙ মাজা। চুল স্ট্রেইট। গোল্ডেন হাইলাইট। অবিকল ওরিজিনাল শ্যামশ্রী।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালভারত -- শেষ ধ্বংসের সন্ধিক্ষণে - Partha Banerjee
২২ এপ্রিল ২০২৪ | ৪৬৪ বার পঠিতপার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক বিশ্লেষণমূলক গ্রন্থ "ভারত -- শেষ ধ্বংসের সন্ধিক্ষণে" (অভিযান পাবলিশার্স, মার্চ ২০২৪)'এর একটি সমালোচনা।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালফারাও-এর দেশে কয়েকদিন - পর্ব ৯ - সুদীপ্ত
২২ এপ্রিল ২০২৪ | ১৩৮ বার পঠিতলাক্সর মন্দির থেকে কার্নাকের মন্দির পর্যন্ত ছিল একটি সুপ্রাচীন রাস্তা, যার নাম ‘Alley of Sphinxes’ বা ‘Avenue of Sphinxes’। এই রাস্তাটি ছিল প্রায় দু-কিলোমিটার দীর্ঘ। আমরা বাস থেকেই দেখলাম সেই রাস্তা আর তার দুপাশে স্ফিংক্স-এর সারি, যদিও অধিকাংশ-ই ভাঙা। বাসের একদিকে রয়েছে লাক্সর মন্দির, অন্যদিকে কার্নাক। আর আমাদের বাস এই অ্যাভিনিউ-এর উপর দিয়ে একটি সেতু পার হয়ে এগিয়ে চলল। এই স্ফিঙ্কস-গুলির কিছু তৈরী হয়েছিল ফারাও তুতানখামুনের আমলে, কিছু তৃতীয় আমেনহোটেপের আমলে আর বাকিটুকু ফারাও প্রথম নেকতানেবো-র সময়ে। প্রায় মিনিট পনেরো পরে আমরা এসে দাঁড়ালাম কার্নাক মন্দিরের পার্কিং-এ।
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাসাদা খাম - দীপেন ভট্টাচার্য
২২ এপ্রিল ২০২৪ | ৪০৮ বার পঠিততার স্ত্রী তাকে ফিরে আসতে না করেছিল, অনেক অনুনয় করেছিল, কিন্তু সে শোনেনি। বিমানবন্দরে নামামাত্রই তাকে আটক করা হয়েছিল। নিয়ে আসা হয়েছিল রাজধানী থেকে বহু দূরে এই বন্দিশিবিরে। সে জানত এরকমই হবে। সকালে তাকে নিয়ে যাওয়া হতো অন্য একটি ঘরে, পার হতে হতো একটি করিডর, এক পাশে দেয়াল, অন্য পাশে পর পর আটটি কামরা, এর মধ্যে একটি ছিল তার। কিন্তু সেটা সে বুঝতে পারত না, কাপড় দিয়ে বাঁধা থাকত চোখ। ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে লাগলে বুঝতে পারত বাড়িটি থেকে সে বের হয়েছে। এর পরে ত্রিশটি পদক্ষেপ, অন্য একটি বাড়িতে ঢোকা। সেখানে একটি ঘরে তাকে চেয়ারে বসিয়ে চোখের বাধন সরিয়ে নেওয়া হতো। মিনিট দশেক অপেক্ষার পর আসত কমিসার। প্রথম দিন সে জিজ্ঞেস করেছিল, ‘আমি কে আপনি জানেন?’ কমিসার বলেছিল, ‘আমি জানি আপনি জনগণের শত্রু, এটুকুই আমার জন্য যথেষ্ট।’ বেশি জানা কমিসারের জন্য ভালো নয়।
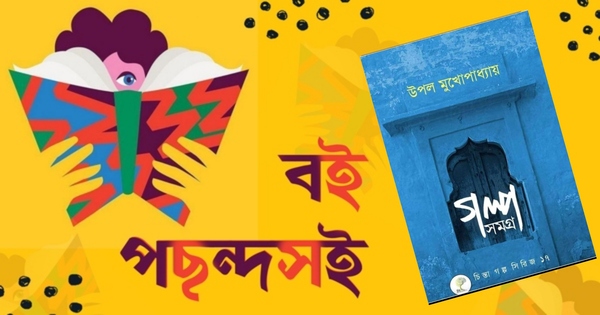 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাগল্পসমগ্র’ (২০২২) প্রথম খণ্ড (উপল মুখোপাধ্যায়) - পুরুষোত্তম সিংহ
২২ এপ্রিল ২০২৪ | ২৭৬ বার পঠিতবিজ্ঞাপনের মোহিনী মায়া, সংবাদের আলো-আঁধারি ভাষা, কুঞ্ঝটিকা, বাজার ধরার কৌশল সমস্ত মিলিয়ে যে ফাঁদ তার প্রগাঢ় ভাষ্য উপল নির্মাণ করে নেন। সেই নির্মাণে গপ্প হিসেবে উপলকে অনেক সময়ই বাস্তবের আড়ালে চলে যেতে হয়। বাস্তবকে ধরে অপ্রচ্ছন্ন বাস্তবের প্রতিমূর্তি গড়ে তোলেন। সেই অপ্রচ্ছন্ন বাস্তবের ছায়ামূর্তির মধ্যেই বাস্তবের প্রতিমা লুকিয়ে আছে। সেখানে পাঠক বাস্তবকে আবিষ্কার করবেন বা প্রত্যাখ্যান করে অধিবাস্তবের স্বরকে দেখবেন সেটা পাঠকের প্রত্যাশার উপর ছেড়ে দেন। পাঠকের ভাষ্যে তা শিল্প হতেও পারে আবার নাও হতে পারে। সেসব নিয়ে উপলের কোনো মাথা ব্যথা নেই। তিনি শিল্প বা না-শিল্প বৃত্তের ভাবনায় পাঠককে যে মাতিয়ে রাখতে পারেছেন সেটাই তাঁর সার্থকতা। হ্যাঁ তিনি রীতিমতো পরীক্ষা নিরীক্ষা করে যান। গদ্যসেতু ধরে ভাবনার তরঙ্গ বিচ্ছুরণে পাঠকের মস্তিষ্কে একাধিক বিরোধাভাসের জাল বুনে দিতে চান। সেখান থেকে পাঠক বাস্তবের সত্যে ফিরুক বা বাস্তবকে অস্বীকার করে শিল্পের সত্য বুঝে নিক।
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাসিন্দবাদের গল্প ছড়ানো ছাদে - সুকান্ত ঘোষ
২২ এপ্রিল ২০২৪ | ১৬৩ বার পঠিতগলির শেষ প্রান্তে একসময় বাজত সুরের রজনীগন্ধা গ্রীষ্মের ক্লান্ত দুপুরে, শীতের মিঠে রোদে ছাদে উঠে মেলে দিত ছাপা কাপড়, ছড়িয়ে যেত রেক্সোনা সাবানের চেনা গন্ধ কৈশোর চাইত আরো একটু গায়ের কাছে যেতে ঘেঁষে যেত ঝুঁকে আসা গাব গাছের পাতা কাটা কাটা ছায়ায় বসে ফিসফিস করে কানের কাছে কেউ বলত নিষিদ্ধ গল্প – একের পর এক শীতের চাদরের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসা দুধ সাদা হাতে আলতা চুঁয়ে পড়া দেখতে বলত মিঠে ফিনফিনে গলা বলত চাদরে জড়িয়ে রাখা আছে সিন্দবাদের গল্পের ঝুলি আলাদিন হবার প্রলোভন দেখাত দুপুরের ছাদ –
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাকবিতাগুচ্ছ - মণিশংকর বিশ্বাস
২২ এপ্রিল ২০২৪ | ৪৬৮ বার পঠিতযারা ভোর-ভোর উঠে স্বাস্থ্যচর্চা করে পার্কে দৌড়ায় ঠিক করে দেখলে আসলে তারা মৃত্যুভয়ে দৌড়ায় একথা লিখেই মনে পড়লো— তুমিও তো ঠিক করে দ্যাখোনি কখনো আমি কেন এভাবে দৌড়ে গেছি তোমার দিকে পড়ে গিয়ে, হোঁচট খেয়ে, আবার হেঁটে গেছি এক বর্ষা আগুনের ভিতর দিয়ে শুধুই তোমার পাবার জন্য!
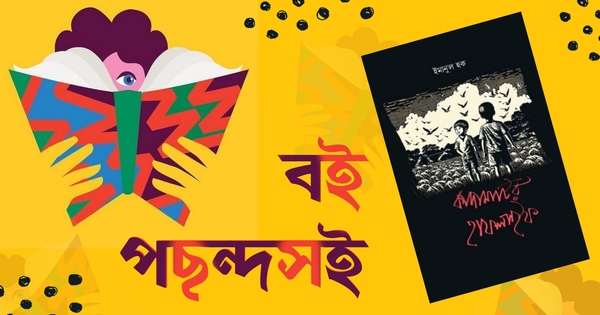 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাপুস্তক সমালোচনা : কাদামাটির হাফলাইফ (ইমানুল হক) - প্রদীপ দাস
২১ এপ্রিল ২০২৪ | ১৮০ বার পঠিতবইটি পড়া শেষ করে মাথায় একটা কথা ঘুরপাক খাচ্ছে এবং মনে হচ্ছে যে এই বইটি না পড়ে মরে গেলে বড্ড অন্যায় হয়ে যেতো। প্রায় প্রতিটি অধ্যায়ের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বারবার মনে হয়েছে যে এই বই আমার জীবনের ফেলে আসা দিনগুলোকে মনে করে লেখা হয়েছে। এই বই আমার একান্ত নিজস্ব জীবন দলিল বললেও হয়তো অত্যুক্তি হবে না। ... ...জীবন মানেই উৎসব, জীবন মানেই সম্ভাবনা। আপনার লেখাগুলো প্রতি মুহূর্তে সেই জীবনেরই জয়গান গেয়েছে। কাদামাটির হাফলাইফ জীবন থেকে শিক্ষা নিয়েই জীবনকে উপলব্ধি করতে শেখাবে, এই বিশ্বাস জারি থাকল।
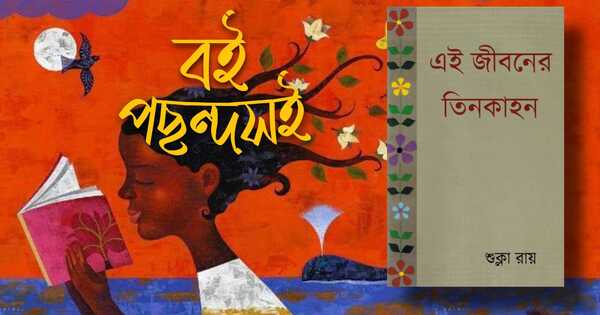 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাএই জীবনের তিনকাহন (শুক্লা রায়) - মালিনী সিদ্ধান্ত
২১ এপ্রিল ২০২৪ | ৪৪৬ বার পঠিতএই জীবনের তিনকাহন-এর প্রথমপর্ব, ‘বাপের বাড়ি’। লেখিকার জন্ম ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে। রাসবিহারী অ্যাভিনিউ-এ বাড়ি। ঠাকুরদা, ঠাকুমা, বাবা, জ্যাঠা, কাকা, পিসি সকলে মিলে বিশাল এক যৌথ পরিবার। চন্দননগরে সংস্কৃত টোল পণ্ডিতের বংশগত জীবিকা ছেড়ে শিক্ষা-চাকরির জন্য ঠাকুরদার কলকাতায়ন। তারপরে কলকাতায় বাড়ি বানিয়ে পাকাপাকি ভাবে বসবাস। বাবা-কাকা-জ্যাঠারা স্ব-স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। কেউ ইঞ্জিনিয়ার, কেউ বা আইনজীবী। বাড়ি ভর্তি ভাই-বোনেরা, আর আছেন গোপালজিউ। সেইজন্য বাড়িতে আমিষ খাবারের প্রচলন নেই। ভাই-বোনেরা মিলে বাড়িটাকে পুরো মাতিয়ে রাখে। কখনও থিয়েটার, কখনও হাতে-লেখা পত্রিকা প্রকাশ, আবার কখনও বা নিখাদ দুষ্টুমি। সঙ্গে বিজয়া, দোল, ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার মতো চিরাচরিত উৎসব পালন তো লেগেই আছে। সেখানেও অবশ্য পারিবারিক বৈশিষ্ট্যের বিশেষ কিছু স্বাক্ষর আছে। অন্দরের অন্তর লেখিকার লেখায় এক নিরবচ্ছিন্ন চিত্রপটে ধরা দিয়েছে।
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাক্যালিডোস্কোপে দেখি - জীবন নাটক - অমিতাভ চক্রবর্ত্তী
২০ এপ্রিল ২০২৪ | ৩৫৩ বার পঠিতরবিবুড়োর ডাকঘর থেকে একটা ছোট অংশ ছিল আমাদের পাঠ্যবইয়ে, অমল ও দইওআলা শিরোনামে। দিদিমণিরা সেটাই বেছে নিলেন মঞ্চস্থ করার জন্য। সম্ভবত: প্রচুর পটর-পটর করার যোগ্যতায় আমি মনোনীত হলাম অমল-এর ভূমিকায়। চতুর্থ শ্রেণীর এক শ্রীমান হল দইওআলা।সেই প্রথম জেনেছিলাম রিহার্সাল কাকে বলে। শেষ ক্লাস-এর পরে শুরু হত। ভাল লাগত, তবে একটু ক্লান্ত হয়ে যেতাম – আমার তো কবে সব মুখস্ত হয়ে গেছে, ভাব ভঙ্গী সহ! দিদিমণিরা মাঝে মাঝে আলোচনা করতেন কেমন করে মঞ্চসজ্জা করলে বা আর কি কি করলে নাটকটা একেবারে সত্যির মত করে তোলা যায়। সেই সব কিছু কিছু শুনে আমার ধারণা হয়েছিল যে আসল অনুষ্ঠানের দিন আমাকে দইওআলা ছেলেটির হাত দিয়ে একটা সত্যি দই-য়ের ভাঁড় দেওয়া হবে। আমার কাছে নাটকের আসল আকর্ষণ ছিল সেটা এবং সেই নিয়ে ভিতরে ভিতরে খুব উৎফুল্ল থাকতাম।
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাপলাণ্ডু সংহিতা - নন্দিনী সেনগুপ্ত
২০ এপ্রিল ২০২৪ | ৩৯২ বার পঠিতএকটা নধর আকারের গোটা পেঁয়াজ, পান্তাভাতের থালার পাশে। এই স্বপ্নটা বিলাস ক’দিন ধরেই দেখছে। আসলে এখন গোটা একটা পেঁয়াজ একবেলায় কে আর খেতে পাবে? অর্ধেক বা সিকিভাগ বরাদ্দ, যা দাম বাড়ল… কিছু করার নেই। বাদ চলেও যেতে পারে একদম। তখন শুধু লঙ্কার আচার দিয়েই… বউ দু’আঙুল দিয়ে যেভাবে সিঁদুর পরত, সেভাবে একটিপ লাল লঙ্কার আচার কৌটো থেকে তুলে নেবে সে।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালদোলজ্যোৎস্নায় শুশুনিয়ায় - ৫ - সমরেশ মুখার্জী
২০ এপ্রিল ২০২৪ | ৮৫ বার পঠিতআশির দশকে যাদবপুরের কয়েকটি ছাত্রছাত্রী শুশুনিয়া পাহাড়ে গেছে শৈলারোহণ অভ্যাস করতে - সেই ভিত্তিতে এই আখ্যান … ঈশু বলে, "দ্যাখ জেঠু, এসব কথা বলতে কিন্তু আমারও খারাপ লাগছে যেমন লাগছে তোর শুনতে। কিন্তু এসব তো বাস্তব সত্য। হয়তো ভবিষ্যত সমাজে এমন অসাম্য, অবিচার থাকবে না। তখন আমাদের মতো কেউ এমন আলোচনা করবে কেবল অতীত বিচ্যূতি পর্যালোচনার জন্য। তবে আমার জীবদ্দশায় তেমন দিন আমি দেখে যেতে পারবো বলে মনে হয় না..
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাবিপ্লবের আগুন - কিশোর ঘোষাল
২০ এপ্রিল ২০২৪ | ২৪৭ বার পঠিতডামল মায়ের দিকে তাকিয়ে চোক নাচিয়ে মুচকি হেসে বলল, “আমার বাপ তোরে কোনদিন কয়েচিল, কোতা যায়, কী করে? শুধোলি কইত “আজকাজ”। আমারও সেই “আজকাজ”। তয় কোন আজা, কেমন আজা, তার আনি কে, সেটি বুলতে পারবনি। আমার বাপও ওই কাজই করত, সে কতা তুই, জানিস। তুই যে ওই ভুঁড়ো-শেয়াল নাদুটাকে ঢিট করেছিলি, সে কতাটা জেনেই বাপ আমার, তোকে-আমাকে ছেড়ে লিশ্চিন্তে বাইরে বাইরে কাজে ফিরতে পারত। তুই আমার বৌ হুলটার বুকেও অমন বল এনে দে দিকিন, মা”। “নে, নে আমারে আর বেশি ভালাই বুলোতি হবে নি। আজকাজ করিস না কি ছাইপাঁশ করিস, বুজি না বাপু। আজার সঙ্গের নোকেরাও দেকেচি – কেমন সোন্দর সাজপোশাক পরে, মাথায় পাগ বাঁধে, গলায় এতএত সোনার হার পরে। তোদের বাপ-ব্যাটার মতো অখদ্দ্যে চেহারার কাউকে কোনদিন দেকিনি”। ডামল অবাক হয়ে বলল, “তুই আবার আজা-আনিদের কবে চাক্ষুষ করলি, মা?”
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাসীমানা - ৪৫ - শেখরনাথ মুখোপাধ্যায়
২০ এপ্রিল ২০২৪ | ৫৪ বার পঠিতনজরুল এবারেও কোন জবাব দেয়নি। সামনে একটা দড়ি-বাঁধা ফাইল, সে খোলে সেটা। একেবারে ওপরের কাগজখানা হাতে তুলে নেয়, যা লেখা আছে কাগজে তাতে চোখ বোলায় একটু, আবার রেখে দেয় ফাইলে। ঘরে আরেকবার ঢোকে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ; এবার একটু দ্রুততর, বলে, মানুষকে কন্ট্রোল করতে পারছে না পুলিশ, ধাক্কাধাক্কি হাতাহাতি চলছে। এবার ধারাবিবরণী একটু বন্ধ করে তোমার কবিতাটা পড়া দরকার। কোনরকমে এই কথাগুলো বলে নিজের একটা হাত সে বাড়িয়ে দেয় নজরুলের দিকে। নজরুল নৃপেনের হাতটা ধরে, ফাইলটাও সঙ্গে নেয়। ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে স্টুডিওর ভেতরে যায় ওরা, পাশাপাশি দুটো চেয়ারে বসে। যে দু'জন মাইকের সামনে বসেছিল, দুজনেরই কানে একটা করে ইয়ারফোন। শবযাত্রার সঙ্গে অতি ধীরগতিতে রেডিওর গাড়ি চলতে চলতে শবযাত্রার যে সংক্ষিপ্ত ধারাবিবরণী সরাসরি পাঠিয়ে দিচ্ছে রেডিওর স্টুডিওয়, ইয়ারফোনে তা শুনে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সম্প্রচারযোগ্য ভাষায় তার তাৎক্ষণিক অনুবাদ করে দুজন ঘোষকের একজন বেতারে তা পাঠিয়ে দিচ্ছে তার নিজস্ব কণ্ঠস্বরে। দ্বিতীয় জন, এখন যে শুধু ইয়ারফোনেই মনোযোগী, চেয়ারে বসে-থাকা নজরুল-নৃপেনের দিকে সে হাত তুলে ইঙ্গিত করতেই নৃপেন কাজির হাতে হাত রাখে। কাজি একটুও সময় নষ্ট না করে পড়তে শুরু করে:
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাকাদামাটির হাফলাইফ - ইট পাথরের জীবন - ইমানুল হক
২০ এপ্রিল ২০২৪ | ২২৬ বার পঠিতআমাদের গ্রাম দ্রাবিড় যুগের গ্রাম। প্রথম খণ্ডেই লিখেছি। মুসলিম বসতি কবে থেকে শুরু সে-নিয়ে পড়া কথা বলা যাবে। গ্রামের ৬৫ শতাংশ মুসলিম। গ্রামে ইদ বকরিদ দুর্গাপূজার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল ওলাইচণ্ডী পূজা আর গাজন। গাজন হতো চৈত্র মাসের শেষদিন। গাজনের দেবতা শিব। শিবকে সবাই মানেন। গ্রামের একমাত্র মন্দির ছিল, শিব মন্দির। তার পুরোহিত গন্তা বেনে। জাতে বেনে। আর গাজনের সন্ন্যাসী বেশিরভাগ মুচি সম্প্রদায়ের। সাতদিন ধরে উপোস করে গাজনের দিনে অনেক উঁচু থেকে ঝাঁপান দিতেন সন্ন্যাসীরা। তার আগে দণ্ডী কেটে আসতেন পুকুর থেকে। চৈত্র মাস। কাঠ ফাটা রোদ। সেই রোদে মাটিতে শুয়ে শুয়ে আসা। সন্ন্যাসীদের দলে থাকতো আমার গৌরদা। বাঙালি যাত্রাপালার নায়ক। সেই দেখে আমি তার অনুরাগী। গৌরদা না খেয়ে শুয়ে আছে, এটা আমাকে খুব কষ্ট দিত। তখন গরম বলে সকালে স্কুল। স্কুল থেকে ফিরে আমি শিব মন্দিরে গিয়ে বসতাম। তখন এসব নিয়ে কোনও ছুঁৎমার্গ ছিল না। গাজনের দিন হতো সবচেয়ে মজা। সবার শেষে অনেক উঁচু থেকে ঝাঁপ দেবে গৌরদা। নীচে কয়েকশো মানুষ। ধরে নেবে। নিয়ে মাথায় তুলে নাচবে। ওরাই তো তখন নায়ক।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালকিষেণজি মৃত্যু রহস্য - পর্ব ৫ - বিতনু চট্টোপাধ্যায়
১৯ এপ্রিল ২০২৪ | ২১৮ বার পঠিতএকদিন সন্ধ্যায় জামবনিতে ঝাড়খন্ড পার্টির এক কর্মী খুন হলেন। প্রায় মাঝরাতে মৃতদেহ উদ্ধার করতে পারল পুলিশ। পরদিন সকাল থেকে এই নিয়ে উত্তেজনা পুরো জামবনি, বিনপুরে। সকালে অফিসে কিছু কাজ ছিল। তা শেষ করে দুপুরে মেদিনীপুর শহর থেকে রওনা দিলাম জামবনির উদ্দেশে। রাস্তায় যেতে যেতেই ওয়্যারলেসে খবর পেলাম বুদ্ধ ভকতের গুলি লেগেছে। তাঁকে ঝাড়গ্রাম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। মুহূর্তের মধ্যে মনে হল, পরিস্থিতি আজ হাতের বাইরে চলে যাবে। আগের রাতে ঝাড়খন্ডি খুন। আর তার বদলায় আজ বুদ্ধ ভকত গুলিবিদ্ধ! বুদ্ধদেব ভকত তখন বিনপুরের সিপিআইএম বিধায়ক।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালজিনগত পাপক্ষয় সহ অন্যান্যরা - ফরিদা
১৯ এপ্রিল ২০২৪ | ১৯৩ বার পঠিত বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাইলেকটোরাল বন্ড, ওষুধের মূল্যবৃদ্ধি এবং আমাদের সহনশীলতার পরীক্ষা - জয়ন্ত ভট্টাচার্য
১৯ এপ্রিল ২০২৪ | ৭০৮ বার পঠিতভোটের ঠিক আগে বিভিন্ন ওষুধ কোম্পানি কত টাকার ইলেকটোরাল বন্ড কিনেছে এ নিয়ে কয়েকদিন আগেও সর্বস্তরের (প্রিন্ট এবং ইলেকট্রোনিক) সংবাদমাধ্যমে বেশ কিছুদিন ধরে খবর হচ্ছিল। ইলেকটোরাল বন্ড এবং ওষুধ কোম্পানির নিবিড় যোগ নিয়ে অনেক লেখা হয়েছে। শিক্ষিত জনতার একটি বড় অংশই, আশা করা যায়, এ বিষয়ে অবহিত। শুধু কিছু তথ্য প্রাসঙ্গিক হবার কারণে যোগ করা যায়। এবং, ভেবে দেখতে হবে, এর সাথে আমাদের দেশের ওষুধনীতি, নির্বাচনী রাজনীতি ও জনস্বাস্থ্যের সংযোগ আছে। ... ... হেটেরো গ্রুপসের মতো একই পরম্পরায় ইন্টাস, লুপিন, ম্যানকাইন্ড, মাইক্রোল্যাবস, টরেন্ট ফার্মা, জাইডাস ফার্মা, গ্লেনমার্ক, সিপলা ইত্যাদি কোম্পানির অফিসে প্রথমে দুর্নীতি ও আর্থিক অনিয়মের জন্য হানা দেওয়া হয় এবং এরপরে সবাই ইলেকটোরাল বন্ড কেনে কোটি কোটি টাকার। ওষুধের দামের ওপরে এর প্রভাব সহজেই অনুময়ে। দান-খয়রাতি করার জন্য এরা টাকা খরচ করেনা। ওষুধের মার্কেটিং (যার মধ্যে ডাক্তারকে দেওয়া উপঢৌকনও আছে) ইত্যাদির জন্য কোটি কোটি খরচ করে। না করলে হয়তো ওষুধের দাম সাধারণ মানুষের আরেকটু নাগালের মধ্যে থাকতে পারত।
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাসীমান্তরেখা - প্রতিভা সরকার
১৯ এপ্রিল ২০২৪ | ২৩০ বার পঠিতকলকাতার মানুষজনেরা এইসবের হুজ্জোতির খবর রাখে না। তাদের মন ভুলোবার হরেক চিজ আছে। এইরকম ঝামেলাওয়ালা জায়গায় দুদিনের ছুটি কাটাতেও কেউ আসে না, যতই জাগ্রত তীর্থস্থান হোক না কেন! এটা একেবারেই সীমান্ত-এলাকা, কাঁটা তারের এ পাশে লাল নিশান ওড়া ভ্রামরী দেবীর মন্দির, খুব জাগ্রত জ্যান্ত তীর্থ, ওপাশে সবুজ মাথাওয়ালা গম্বুজ, সোনা পীরের থান। মানত রাখলে নাকি কেউ খালি হাতে ফেরে না। দুপাশেই যতদূর চোখ যায় সবুজ খেত, যার বুক চিরে দৌড়ে চলে গেছে মানুষ সমান কাঁটাতার। ছুঁচলো কাঁটা, খুব শক্ত তার, আর দবেজ। সেই ছুটন্ত তারের লাইন বরাবর রাতবিরেতে বুটজুতোর মসমস, সন্দেহ জাগলেই ঘন ঘন হুইসিলের আওয়াজ। তবে তাতে কী আর কিছু বন্ধ থাকে! যার যা করার সে তাই করে যায়, কাজের মতো কাজকাম চলে, নদীর মতো নদী বহে যায়। শুধু মাঝেমধ্যে কাঁটাতারের এপাশে ওপাশে আচমকা দুম শব্দের সঙ্গে লাশ পড়ে। চাপা আর্তনাদ, দৌড়োদৌড়ির শব্দ। তারপর সব চুপচাপ।
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাশেষের কবিতা - দীপ্তেন
১৯ এপ্রিল ২০২৪ | ১৮৮ বার পঠিতহলুদ ফুল ছিলো চোখের পাতা ছুঁয়ে শহরও আলোময় পাপে ও উত্তাপে সে ছিলো মধুমাস, মেলাতে কত লোক কেনো যে স্মৃতিরতি, কেনো যে নীরবতা কেনো যে মনে পড়ে, পাথুরে অবকাশে
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাহন্য - সৈয়দ তৌশিফ আহমেদ
১৯ এপ্রিল ২০২৪ | ২৬৩ বার পঠিতপ্রশ্নটা হল, কিভাবে নিকেশ করবে আমায় ? গলা টিপে শ্বাসরোধের সাবেকি পন্থায়? আমার কুতকুতে চোখগুলো কি তখন বল্লমে গাঁথা শুয়োরের মতো ঠিকরে বেড়িয়ে আসবে ? মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও বিস্ফারিত দৃষ্টি প্রাণপণে ধরে রাখতে চাইবে আততায়ীর শেষ ছবি? নাকি মরবো খাদ্যে বিষক্রিয়ার মতো দীর্ঘ যন্ত্রণাময় কদর্য কায়দায়? কাটা পাঁঠার মতো জগঝম্প জুড়ে, শ্বেত পাথরের তেলা মেঝেয় বমি -পায়খানায় একাকার হয়ে ? আর নাকি প্রকাশ্য রাস্তায় পয়েন্ট ব্ল্যাংক রেঞ্জের গরম বুলেট ফুঁড়ে দিয়ে যাবে মগজ? কিছু রক্তমাখা ঘিলু ছিটকে গিয়ে লাগবে কি কোন বেনামী ল্যাম্পপোস্টের গায়ে? কে জানে হয়তো দু একটা অশ্লীল স্মৃতিও তখন গড়িয়ে নামলো পোস্টের গা থেকে। আমার পড়ে থাকা নিথর লাশের দিকে চেয়ে রাস্তার লোক কি চমকাবে খুব? খুব ? বোধহয় পুরনো প্রফেসিকে সমর্থন জানিয়ে বলে উঠবে, – এ তো জানাই ছিল! আজ নয়তো কাল এটা হওয়ারই কথা! বেশ হয়েছে শালা!
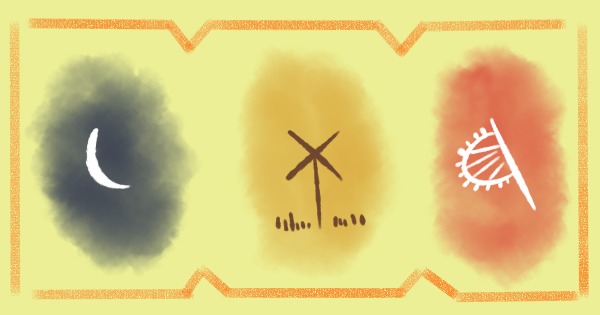 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাদৌড়বাজ হাউসকীপার - সমরেশ মুখোপাধ্যায়
১৯ এপ্রিল ২০২৪ | ১৬৬ বার পঠিতসলিলের পড়াশোনায় মাথা ছিল না। তাই মাধ্যমিকের পর কাকা ওকে একটা বিলেতি মালিকানাধীন ফ্যাক্টরিতে হেল্পার হিসাবে ঢুকিয়ে দিলেন। সুপারিশ ছাড়া ওখানে ঢোকা মুশকিল। কাকা বলেছিলেন, পড়ায় যখন তোর ইচ্ছা নেই ভালো করে হাতের কাজটা শেখ। সেটা মন দিয়েই শিখেছিল সলিল। ফলে ক্রমশ হেল্পার থেকে মেকানিকে পদোন্নতি হোলো। মাইনে, ওভারটাইম মিলিয়ে রোজগার মন্দ নয়। তিনকূলে ঐ কাকাই সলিলের একমাত্র আপনজন। কাকার বাড়ীতেই ছোট থেকে মানুষ। কাকার অবস্থা ভালো। মনটাও দরাজ। তাই চাকরি পাওয়ার পরেও সলিলের থেকে এক পয়সাও নিতেন না তিনি। বলতেন, আমি আর কদিন, পয়সা জমা, তোর একটা নিজের মাথা গোঁজার ঠাঁই তো দরকার।
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালবৈঠকি আড্ডায় ১৩ - হীরেন সিংহরায়
১৮ এপ্রিল ২০২৪ | ১৭১ বার পঠিতজার্মানির ভাবী পরিত্রাতার দুর্বার জয়রথ ছুটে চলে সারা দেশে । মন্ত্রমুগ্ধ জনতা সভায় হাজির হয় তাঁর দুটো কথা শোনার জন্য – তিনি বারবার বলেন, ক্ষমতায় এলে তিনি জার্মানিকে ফিরিয়ে দেবেন তার গর্ব, ষাট লক্ষ বেকার মানুষকে দেবেন কাজের সুযোগ , দেশ গড়বেন নতুন করে । যুদ্ধে পরাজিত অপমানিত জার্মান জাতিকে দেবেন সামরিক সক্ষমতা । তারা আবার মাথা তুলে জগতসভায় দাঁড়াবে। জনতা তাঁর মুখনিঃসৃত প্রতিটি শব্দকে আঁকড়ে ধরে । তাদের নিজস্ব ভাবনা চিন্তা লুপ্ত হয়েছে । নেতা একবার থামেন । জনতা দাবি করে আরও কিছু বলুন, আগে কহ আর । লক্ষ কি ? এক বিপক্ষ এবং সকল প্রতিরোধকে নির্মূলে বিনাশ করা দুই ভাইমারে তৈরি সাংবিধানিক বেড়াজাল চূর্ণ করা তিন এমন এক দেশ গঠন করা যা হবে হাজার বছর স্থায়ী তৃতীয় সাম্রাজ্য ( থার্ড রাইখ )
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাটুনিমুনির জীবন - দময়ন্তী
১৮ এপ্রিল ২০২৪ | ৮১৮ বার পঠিত‘আমি কক্ষনো অন্য কারুর জন্য কাঁদি নি জানো। যতবারই কেঁদেছি তা কেবল নিজের জন্য, নিজের না পাওয়া, ক্ষোভ, দুঃখ থেকে চোখে জল এসেছে। বাবা মা মারা যাওয়ার পরেও না, দাদা বৌদি সম্পর্ক কেটে চলে যাওয়ার পরেও না।‘ প্রায় একদমে বলে ফেলে একটু থমকে যায় ও, আঁচল ঘুরিয়ে এনে মুখটা মোছে। মাঝারি হাইটের গাঁট্টাগোট্টা মেয়েটির নাম দেওয়া যাক ‘আমি’। ... ... ‘তুমি যেমন অন্যের জন্যে কাঁদো নি কখনো আমার ঠিক তার উলটো। আমি নিজের লোকদের জন্য মাসের পর মাস কেঁদেছি, পাড়ার লোক যাদের রোজ দেখি তাদের কারুর কিছু হলেও কেঁদেছি। এমনকি কাগজে, টিভিতে কোথাও আগুন লেগে, জলে ডুবে, বিল্ডিং ভেঙে, ঝড়ে বন্যায় মানুষ মারা যাবার খবরেও হাউ হাউ করে কেঁদেছি। সেই থেকেই আমার নাম হয়ে গেছে খোলাকল। ... ... লম্বা চওড়া খেলোয়াড়ি ধরণের চেহারার মেয়েটির নাম দেওয়া যাক ‘তুমি’। ... ... সে মুখে একটা মিচকে হাসি ঝুলিয়ে চুপচাপ দেখছিল এদের। আমি বা তুমি কেউ কোন কথা বলছে না দেখে আস্তে করে গলা খাঁকারি দিল।
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাআব্বু আব্বা বাবা - মাজুল হাসান
১৮ এপ্রিল ২০২৪ | ২৮৩ বার পঠিতশব্দহীন সাইকেল আসে৷ বেল বাজেনি ক্রিং৷ বেল বেজেছে ক্রিং। ঘরঘর করে আহ্লাদে ডেকে ওঠেনি পোষ মাদীটা। টের পায় সাড়ে তিন বছর৷ খুলে দেয় কাঠের পৌনে চার ফুটে হুড়কা আর চেয়ার টেনে ছয় ফুট উঁচুতে লোহার ছিটকিনী৷ "আব্বু আসছে"৷ এইবার গলাগলি ঘুম- ফজর আমার.. ফিশফিশানি দুপুর আসে৷ রঙিন ফড়িং, বোয়ামে নীল চোপড়া মাছ! ঘুম আর ভলো লাগে না৷ মনেহয় দিনমান খেলি "ঘুঘু'র তোর তরকারি" খেলতে খেলতে জহর গড়িয়ে আছর৷ পালানো বাছুর। সুতো ছিড়া ঘুড়ি৷ সন্ধ্যায় রুলটানা খাতা বেঁকে বেঁকে যায়৷ ক্লাস ফাইভের পদ্য লেখার রোগ…
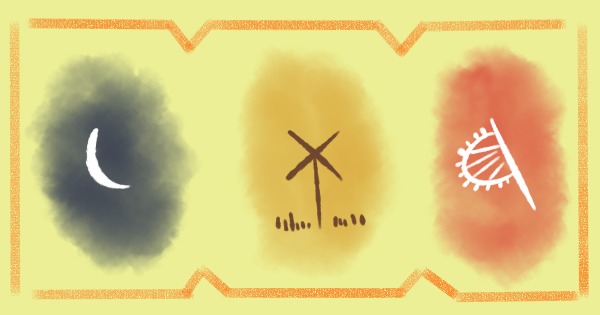 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাসারেতে থাই নববর্ষ - হীরেন সিংহরায়
১৮ এপ্রিল ২০২৪ | ১৯৭ বার পঠিতথাইল্যান্ডে দোল নেই। কিন্তু নববর্ষের দিনে আছে জল ছোঁড়াছুঁড়ির খেলা। এপ্রিল মাসে বেজায় গরম। লাওস কামবোদিয়া থাইল্যান্ডের পথে ঘাটে সেদিন জল আক্রমণের ধুম পড়ে যায়; মারো পিচকারি! সেটা ছবিতে মাত্র দেখেছি। আমাদের এই মন্দিরে তার একটা ছোটো এডিশন আছে – এক ভিক্ষু ঝ্যাঁটা দিয়ে সবার মাথায় জল ছড়িয়ে দেন। দুঃখের বিষয় যে থাইল্যান্ড বা লাওসের স্টাইলে আমরা তাঁকে জল কামান দিয়ে আক্রমণ করতে বা তাঁকে পাল্টা ঝাপটা মারতে পারি না! নববর্ষের পরবের অন্য রিচুয়ালগুলি মোটামুটি অনুসরণ করা হয়ে থাকে ন্যাপহিলের অনুষ্ঠানে - যেমন প্রার্থনার পরে ভিক্ষুদের খাদ্য দ্রব্য দান। সকলে আনেন কিছু না কিছু, সার দিয়ে বসে থাকেন দানের জন্য, ভিক্ষু সেটি গ্রহণ করলে পরেই স্থান ত্যাগ করতে পারেন। অল্প বয়েসি ছেলে মেয়েরা বয়স্ক নারী ও পুরুষের পা ধুইয়ে দেন, পিতা মাতার গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধার প্রতীক সেটি। পুণ্য অর্জনের আরেকটি পন্থা - বুদ্ধ মন্দির বা স্তূপ নির্মাণে শ্রমদান। মাঠের মধ্যে বালি দিয়ে তৈরি স্তূপ মন্দির আছে, দূরে এক কোনায় রাখা বালির পাহাড়; সেখান থেকে পাত্র ভরে কিছুটা বালি এই নির্মীয়মাণ মন্দিরে পৌঁছে দেওয়াটা একটা সিম্বলিক সহায়তা। নববর্ষের এই দিনে নতুন জামা পরা আবশ্যিক, নিজের বা পরিবারের জন্য অর্থ ব্যয় কম,দান বেশি এবং মদ্যপান বারণ!
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালযদি ডাকে লিন্ডসে ! - সমরেশ মুখার্জী
১৮ এপ্রিল ২০২৪ | ২০৫ বার পঠিতআসবে তুমি ইস্ট কোস্টে - একটু আগে জানিয়ে - তখন আমি জর্জিয়া, মেইন, মেরিল্যান্ড, ভার্জিনিয়া, নর্থ ক্যারোলাইনা যেখানেই থাকি। খামোখা পশ্চিম উপকূলে একদা বান্ধবীর কাছে কদিনের জন্য গিয়ে কী করবে? অতীত সুরের সাথে বর্তমান ছন্দ মিলবে না। তাল কেটে মন খারাপ হবে। মনে রেখো It is not wise to travel down the memory lane. Take it easy. Take care, Lindsey"
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাও চাঁদ - সেমিমা হাকিম
১৭ এপ্রিল ২০২৪ | ৪০৩ বার পঠিতআমরা দেশের বাড়ি যেতুম ২৯ শের রোজায়। সন্ধ্যায় চাঁদ দেখা গেলে পরদিন ঈদ নয়ত আর একদিন মানে তিরিশটি রোজা সম্পূর্ণ করে ঈদ পালন। তখন আর চাঁদ দেখার ঝামেলা নেই। হাদিস মোতাবেক তিরিশটি রোজা হয়ে গেলে অবশ্যই পরদিন ঈদ। এখন যেমন,"যাহ! সৌদিতে আগে ঈদ হয়ে গেল। আমাদের হল না কেন?” বলে বিভিন্ন বিতণ্ডার শুরু তখন সেসব কেউ ভাবতও না। চাঁদ দেখা গেলে ঈদ হবে সেই অঞ্চলে নয়ত রেডিওয় কান পেতে থাকতেন মুরুব্বিরা- নাখোদা মসজিদের ইমামসাহেব যা ঘোষণা করবেন মেনে নিতেন সবাই।
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাউপগ্রহ - অমিত চট্টোপাধ্যায়
১৭ এপ্রিল ২০২৪ | ১২১ বার পঠিতসে আমাদের ভুল বানানের চিঠি, সে আমাদের মুগ্ধ চেয়ে থাকা। পাখির ডানায় শেষ বিকেলের আলোয় রাখাল সাজার পাতার বাঁশি রাখা। সে আমাদের গোপন বনলতা, সে আমাদের লুকিয়ে রাখা আলো।
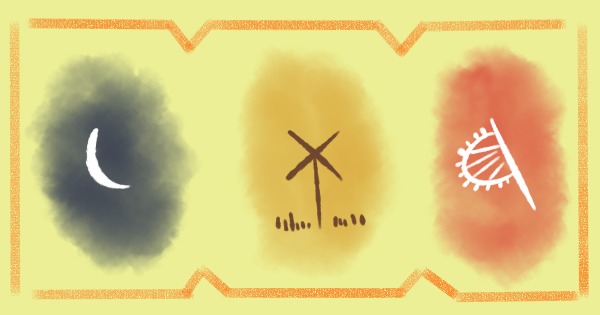 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাকোশিশ কিজিয়ে - কিশোর ঘোষাল
১৭ এপ্রিল ২০২৪ | ৩১১ বার পঠিত“বহনোঁ অওর ভাইয়োঁ...আজ আমরা যে বিষয় শিখবো – সে বিষয় প্রত্যেক লেডিস ও জেন্টসের পক্ষে অত্যন্ত জরুরী শিক্ষণীয় বিষয়। পরন্তু আমাদের দেশে যে শিক্ষাবেওস্থা আছে, তাতে এই শিক্ষা আমাদের দেওয়া হয় না। আমাদের দেশের বাচ্চারা পচ্চিমদেশের অনুকরণ করে যে শিক্ষা লাভ করে, তাতে তারা যে শুধু ভোগময় জীবনের প্রতি লালচি হয় তাই নয়, বরং পাপের দিকে নিরন্তর দৌড়তে থাকে। তারা কদাপি মনমে শান্তি পায় না, দিনরাত পয়সা, প্রমোশন, আলিসান ফ্ল্যাট, লেটেস্ট মডেলের দামি গাড়ি, বছরে একবার ফোরেন টুরের স্বপ্ন দেখতে দেখতে, অন্দরসে খোকলা হয়ে যায়, পরেসান হতে থাকে। বাড়তে থাকে স্ট্রেস – মান্সিক চাপ। মেরেকো আকসর পুছা যাতা হ্যায়, বাবা, ইস সে ক্যায়সে মিলেগি ছুটকারা? কেয়া মুক্তি কি কোই ভি উপায় নেহি হ্যায়? আমি বলি, কিঁউ নেহি, বেটা, অবশ্য উপায় হ্যায়। .."
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালবৈঠকি আড্ডায় ১২ - হীরেন সিংহরায়
১৬ এপ্রিল ২০২৪ | ৩১৪ বার পঠিতদক্ষিণ দিক থেকে উদিত হলেন এক অস্ট্রিয়ান নাগরিক , যুদ্ধে কর্পোরাল হয়েছিলেন , দ্বিতীয় শ্রেণির আয়রন ক্রস ঝোলানো থাকে গলায় । মিউনিকের পাবে তাঁর বক্তিমে শুনতে ভিড় জমে যায় ( হোফব্রয় হাউসের তিনতলায় সেই হলটি দেখতে পাবেন ) ; তাঁর মতে জার্মানি একটা জেতা গেমে হেরেছে কারণ সৈন্য বাহিনীর পিছন থেকে ছুরি মারা হয় । তার জন্য দায়ী কমিউনিস্ট , ইহুদি ও কিছু চক্রান্তকারী বিদেশি । ৯ নভেম্বর ১৯২৩ শখানেক লোক যোগাড় করে ব্যাভেরিয়ার রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের ব্যর্থ অভ্যুথানের পরে গ্রেপ্তার হলেন সেই নেতা , আডলফ হিটলার । সশস্ত্র রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধে পাঁচ বছরের সাজা হয়েছিল ১৯২৩ সালে কিন্তু কোন অজানা কারণে তাঁর রেহাই হল নয় মাস বাদে । ২৭শে জানুয়ারি ১৯৩১ ডুসেলডরফের হর্ম্য মণ্ডিত ইন্দুস্ত্রি ক্লুবের মঞ্চে দাঁড়িয়ে ফ্রিতস থুসেন সমবেত ধনপতিদের উদ্দেশ্যে বললেন, আমাদের দেশের ভাবি পরিত্রাতার সঙ্গে আপনাদের আলাপ করিয়ে দিই -ইনি আডলফ হিটলার । লম্বা বক্তৃতা দেবার অভ্যেসটি ত্যাগ করে হিটলার মাত্র দশ মিনিট বললেন
 হরিদাস পাল
হরিদাস পালকাইজার গান্ধী - Nabhajit
১৬ এপ্রিল ২০২৪ | ১১৪ বার পঠিত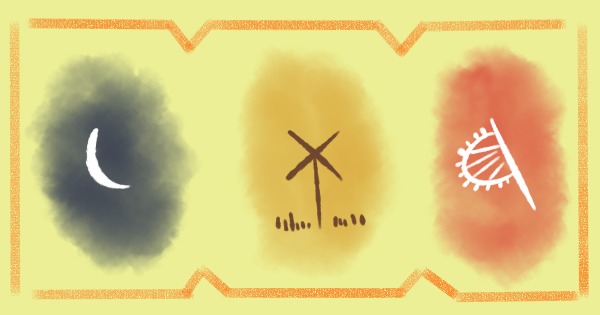 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাওয়েথসাম - উপল মুখোপাধ্যায়
১৬ এপ্রিল ২০২৪ | ৩৮৫ বার পঠিতঅহনা হাঁটতে আরম্ভ করে দিল। সে হাঁটতে হাঁটতে পাহাড়ের খাঁজে চলে গেল। দু পাহাড় যেখানে জোড় খেয়েছে আর দুটো দেশ তৈরি হয়েছে গাছেদের। হ্যাঁ, গাছেদের আর বৃষ্টিদের। সেখানে প্রপাতের শব্দ শোনা যাচ্ছে। সেইখানে অহনাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখব বলে বলে ভাবছি আর দেখি সে অন্য একজনের সঙ্গে কথা বলতে বলতে হাঁটা দিয়েছে। আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। অনেকটা পাহাড় দেখার মত এক দূরত্ব। মনে হয় কাছে কিন্তু দূরত্বটা বেশ। যত কাছে যাওয়া যায় ততো দূরত্বটা থেকে যেতে থাকে, থেকে যেতে থাক – দূরত্বটা শেষ হয় না। বোঝা যায় না পাহাড়টা দূরে, বোঝা যায় না পাহাড়টা কাছে এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি হয়। সে রকমই হচ্ছিল। আমি বুঝতে পারছিলাম না জোরে কথা বলব না আস্তে কথা বলব। তাই দেখতে লাগলাম। প্রথমে গাছেদের এ ওর পাশে পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি। তারা ফুল দেয় না আর দিলেও দেখাতে চায় না যে ফুল দিয়েছে। ছোট ছোট গাছ না কিন্তু তাদের ছোট ছোট লাগে। পাশে একটা বড়ো গাছ ছিল। সেই গাছ দেখে আশ্বস্ত হয়েছি, সেখানে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। হঠাৎ দেখলাম গাছ কথা কইছে আর আওয়াজ হচ্ছে কথাদের।
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাতিনটি কবিতা - অরিত্র চ্যাটার্জি
১৬ এপ্রিল ২০২৪ | ২৪০ বার পঠিতভালোবাসার কাছে যদি পারো, খুলে রেখো তোমার মুখোশ ও দস্তানা এসব এমন, এমনই একটা সময় যখন নিজের কাছে নিজের উপস্থিতি সন্দিগ্ধ ঠেকছে খুব খানিক তফাত রেখে তোমায় নিরীক্ষণ করছে তোমারই পাথরের অবয়ব, ওই তার চোখের মণিহীন চাউনি, ধারালো পেরেকপ্রবণ দৃষ্টিতে দূরের নীলাকাশে, অনাগত মেঘের মত ওই তোমার ছায়া লম্বালম্বি বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে দেখো, সবুজাভ দেওয়ালের গায়ে লেগে থাকা তার টুকরো হাতের ছাপ, অঙ্গ ও মাংসপেশি,
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাফকির ফয়জুল্লাহ - সপ্তম পর্ব - মুরাদুল ইসলাম
১৬ এপ্রিল ২০২৪ | ২৪৬ বার পঠিততালাশ মাহমুদ ভ্রূ কুঁচকে বললেন, আপনে এসবে বিশ্বাস করেন? দ্বিজদাস বললেন, বিশ্বাস অবিশ্বাস পরের ব্যাপার। কিন্তু ব্যাপারগুলা তো আপনারই কাজের বিষয়। ঠিক কি না? তালাশ মাহমুদ বললেন, তা ঠিক। কিন্তু আমি যুক্তি দিয়ে বিচার করে সমাধান করতে চেষ্টা করি। সব সময় যে পারি সমাধানে যেতে এমন না। তালাশ মাহমুদ খেয়াল করলেন দ্বিজদাস একটু ইতস্তত করছেন। পুলিশের একজন বিভাগীয় প্রধান কালু সর্দারের খুনের জন্য এই গ্রামে এসেছেন তালাশ মাহমুদ বিশ্বাস করেন না। তার আসার অন্য কোন কারণ আছে। তালাশ মাহমুদ সেটা বুঝার চেষ্টা করছিলেন। দ্বিজদাস এই সময়ে বললেন, পৃথিবীতে ভালোর শক্তি শেষ হয়ে যাচ্ছে মাহমুদ সাহেব। সব আপনার যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারবেন না। এই যুদ্ধটা না লাগলেও হতো। তাছাড়া আমাদের দেশের দিকেই দেখেন, কেমন অশান্ত পরিস্থিতি। ঢাকায় বড় ঝামেলা হবে আভাস পেলাম। স্যারের এই সময়ে ঢাকায় থাকা দরকার। স্যারকে অনুরোধ করলাম। কিন্তু তিনি এখানে একটা বড় আয়োজনে আটকা পড়ে গেছেন। আপনি কি উনাকে একবার রিকুয়েস্ট করবেন আমাদের হয়ে? তালাশ মাহমুদ বললেন, আমার কথা তো উনি শুনবেন না। আর এখানের আয়োজন একাই সামাল দিচ্ছেন। তাও, আমি বলে দেখব। ঢাকায় কী নিয়ে ঝামেলা হবে বলছেন?
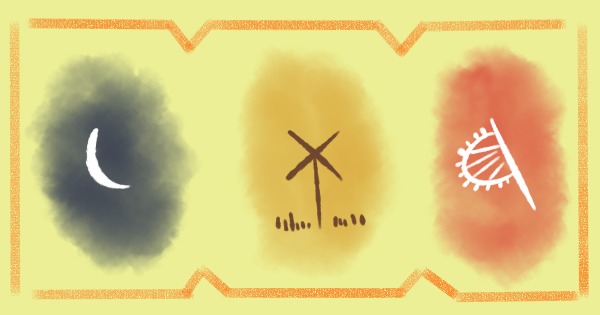 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাএই ঘুম শারীরবৃত্তীয় - দীপাঞ্জন মুখোপাধ্যায়
১৫ এপ্রিল ২০২৪ | ৫৩২ বার পঠিতএগারোটার সময় মৌলিকের অফিসের শেষ ডিনার পাওয়া যায়। তারপর শুধু এককোণে কফি, কেক, স্যান্ডউইচ ইত্যাদির কাউন্টারে একজন বসে বাকি রাত ঝিমোয় আর খুচরো প্যাকেটের চানাচুর, মধু মেশানো ওট বার উগরে দেওয়া ভেন্ডিং যন্ত্রগুলোতে সারারাত কাঁচের ভেতর নীল আলো জ্বলে থাকে। কিউ আর স্ক্যান করে টাকা দিলেই প্যাঁচানো স্প্রিং ধাক্কা মেরে কাঙ্খিত প্যাকেটকে নীচে ফেলে দেয়। রাতে কাজ করা বাধ্যতামূলক নয় অথচ রাতে একজন থাকলে ভালো হয়, সমুদ্রের ওপার থেকে বারো ঘণ্টা এগিয়ে থাকা দেশ থেকে ভেসে আসা এমনই অনুরোধ। এই শিফটে কেউ রাজি হলে প্রতি রাতে অতিরিক্ত টাকা, বিনামূল্যে খাবার এবং যাওয়া আসার গাড়ি পাওয়া যায়। রাত দশটা থেকে ভোর ছটা এই শিফটটাকে দিনের বেলা অফিসের বাকি সবাই বলে গোরস্থানের সময়।
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাপাঁচটি কবিতা - অমিতরূপ চক্রবর্তী
১৫ এপ্রিল ২০২৪ | ১৩১ বার পঠিতকোনো সমুদ্রের হোটেলে বন্ধ ঘরের মধ্যে আমি মরে গেছি। ধরো, সেসময় ভোর পেরিয়ে সকাল। ঘরের জানালার কাচে বাইরের সাদা আলো। প্রতিদ্বন্দী অন্য হোটেলের ঘরগুলিতে যারা আছে- যেসব সংসার অথবা একলা মানুষ, তারা এসময় জেগে উঠে প্রকৃতির টানে হয়তো বাথরুমে, হয়তো নির্ভার হয়ে এসে বিছানায়। কেউ রাতের কোঁকড়ানো চুল চিরুনি লাগিয়ে সোজা করছে, কেউ ভুল মোজা ভুল পায়ে পরে তা আবার সংশোধন করছে। সমুদ্রে ঢেউ উঠে পাড়ে ছুটে আসছে পরপর। সকালের নরম, শীতল ঢেউ। সৈকত নির্জন। শুধু বিগতদিনের আস্ফালন, রক্তপাত বা ধস্তাধস্তির ছাপ বালিতে লেগে আছে। জীবন্ত হয়ে আছে পাশাপাশি হেঁটে যাওয়া দুইজোড়া পায়ের ছাপ। বহুদূর তারা পাশাপাশি হেঁটে গিয়ে বাঁক নিয়ে কোথাও অদৃশ্য হয়েছে। ঝাউবন ঠাণ্ডা। তার গোড়ায় গোড়ায় পরিষ্কার বালি। হোটেলের ডেস্কে যে মানুষ কর্তব্য সামলাতে এইমাত্র এসে বসল, সে এখানে আসার আগে বাতাসে তার শেষ হাই ত্যাগ করে এসেছে। সমুদ্রের হোটেলে যে মেয়েরা আছে, এখন তাদের জল দিয়ে ধোয়া পরিচ্ছন্ন যোনি। জামার নীচে শান্ত স্তন। যেসব পুরুষেরা দিগ্বিজয় করে এখানে এসেছে, তাদের পুরুষ্ট লিঙ্গ এখন মৌনসাধকের মতো ক্ষমাশীল। তাদের মুখগহ্বরে শুদ্ধ আত্মার গন্ধ। তাদের আঙুলের গাঁটে বাদশাহের মতো অসংখ্য চুনি-পান্নার আংটি সকালের আলোয় ঝিকমিক করছে
 বুলবুলভাজা
বুলবুলভাজাফকির ফয়জুল্লাহ - ষষ্ঠ পর্ব - মুরাদুল ইসলাম
১৫ এপ্রিল ২০২৪ | ১৩২ বার পঠিতফকির ফয়জুল্লা বলতে থাকলেন, এই ফকির ফয়জুল্লা সময়ে সময়ে, স্থানে স্থানে ঘুইরা এইখানে আসছে, আর তোরা তারে বাইর কইরা দিবি? কয়দিনের জিন্দেগী তদের? কারে কী কস? সব ক'টারে একবারে খাইয়া ফেলবো! পুরা জঙ্গল যেন গম গম করছিলো ফকির ফয়জুল্লার স্বরে। উপস্থিত সবাই স্তব্ধ হয়ে গেলো। তালাশ মাহমুদের দিকে তাকিয়ে ফকির ফয়জুল্লাহ বললেন, এদের নিয়া যান। কী বালের তদন্ত করেন আপনে? কোন প্রমাণে এখানে আসছেন দলবল নিয়া? প্রমাণ থাকলে আইসেন, আমি নিজেই ধরা দিব। তালাশ মাহমুদ বললেন, কিন্তু আপনে কে? এই গ্রামে কী করছেন? ফকির ফয়জুল্লা বললেন, আমি কে এইটা জানতে কি আসছেন দলবল নিয়া? আমি ফকির ফয়জুল্লা, আমি স্থানে স্থানে ঘুরি, সময় থেকে সময়ে গতান্তরিত হই। আমার কাজ শেষ হওয়ার আগে আমারে কেউ সরাইতে পারব না। এইখান থেকে দূর হন। ফকির ফয়জুল্লা উত্তরের অপেক্ষা না করে, তাদের তাচ্ছিল্য করেই ভেতরে চলে গেলেন।
- আরও বুলবুলভাজা ... আরও হরিদাস পাল ...
-
গুরুচণ্ডা৯-র গ্রাহক হোন
কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে গুরুচণ্ডা৯-র গ্রাহক হোন। গুরুচণ্ডা৯তে প্রকাশিত লেখাগুলি পেতে চাইলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যুক্ত হোন, অথবা, আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলটির গ্রাহক হোন।
- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই
- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... )
(লিখছেন... অরিন)
(লিখছেন... kk, রমিত চট্টোপাধ্যায়, বিপ্লব রহমান)
(লিখছেন... Aranya )
(লিখছেন... পাপাঙ্গুল)
- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন
(লিখছেন... সৃষ্টিছাড়া, সমরেশ মুখার্জী)
(লিখছেন... Prabhas Sen, Ranjan Roy, পড়ুন)
(লিখছেন... সমরেশ মুখার্জী, Kishore Ghosal, সমরেশ মুখার্জী)
(লিখছেন... Muhammad Sadequzzaman Sharif, Muhammad Sadequzzaman Sharif, দীপ)
(লিখছেন... dc, পলিটিশিয়ান, dc)
- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... পাপাঙ্গুল)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... jsl)
(লিখছেন... অরিন, &/, অরিন)
(লিখছেন... lcm, পাঠক, সুকি)
- কি, কেন, ইত্যাদি
- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...
- আমাদের কথা
- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...
- বুলবুলভাজা
- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...
- হরিদাস পালেরা
- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...
- টইপত্তর
- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...
- ভাটিয়া৯
- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...